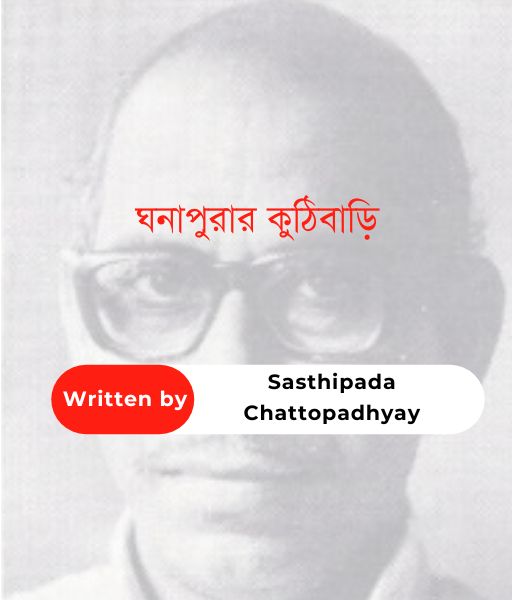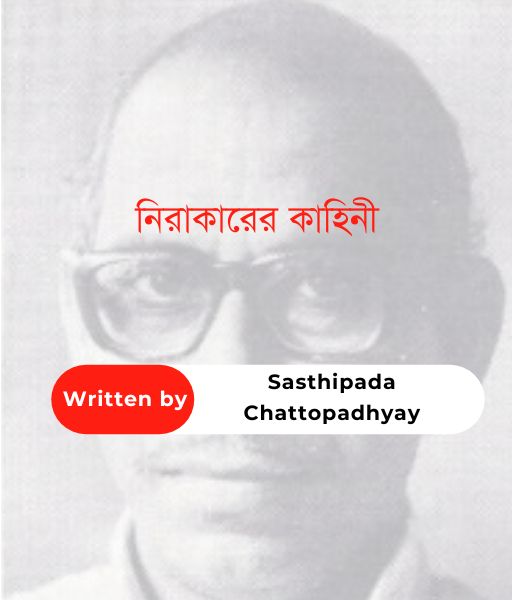লক্ষ্মী আচার্যির গল্প
হরিহরডাঙার চর।
একদিকে নাড়ুগ্রাম, অন্যদিকে ভ্যালাইগাছি। মধ্যে বাবুর মায়ের মরা খাল। এই মরা খালের ওপারে মরা ঘাট। অর্থাৎ হরিহরডাঙার চর। তবে হরিহরডাঙা কেউ বলে না। বলে হরারডাঙা।
সেই হরারডাঙার চরে লক্ষ্মী আচার্যি রোজ রাত্রিবেলা ভূতের কাঁধে চেপে জপ করতে যেতেন। আর ফিরে আসতেন প্রায় মাঝরাতে ভূতের কাঁধে চেপে। তিনি ছিলেন মস্ত গুনিন। তাঁর মতো গুনিন এ তল্লাটে কেন, গোটা বর্ধমান জেলাটার মধ্যে আর কেউ ছিল কিনা সন্দেহ। মন্ত্রের শক্তিতে ভূতকে তিনি বেঁধে রেখেছিলেন। পান থেকে চুন খসবার আগেই ভূতেরা তাঁর সব হুকুম তামিল করে দিত। তাঁকে পালকিতে বসিয়ে সেই পালকি কাঁধে করে বইত। অনেকেই নাকি আড়ালে আবডালে লুকিয়ে দেখেছে এ দৃশ্য। ছায়া ছায়া কালো কালো কী বিচ্ছিরি সব চেহারা! কেউ দেখেছে আস্ত কঙ্কাল। কেউ বা কিছুই দেখেনি। শুধু মাঠের ওপর দিয়ে দুলকি তালে দুলে দুলে যেতে দেখেছে পালকিটাকে। সেই পালকির ভেতরে বসে আছেন গুনিনের সেরা গুনিন—লক্ষ্মী আচার্যি।
সবাই বলে, লক্ষ্মী আচার্যি নাকি পিশাচসিদ্ধ লোক।
চেহারাটিও তেমনই—এই লম্বাচওড়া দশাসই চেহারা। খুব কম করেও সাড়ে ছ’ ফুটের বেশি হবেন তবু কম নয়।
ঘন কালো গায়ের রং।
পরনে লাল চেলি। রক্তবস্ত্র। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। চাঁড়ালের হাড়, শকুনির হাড়, ধনেশ পাখির হাড়ের মালা। নানারকমের লাল নীল পুঁতি, গাছের শিকড় আর কড়ির মালা। কতরকমের দুষ্প্রাপ্য তবলকি। কপালে ডগডগ করত তেল সিঁদুর। লম্বা করে টানা। মাথায় মস্ত টাক। চোখদুটি লাল। রক্তবর্ণ। যেন ভাঁটার মতো জ্বলছে। চোখ উঠলে যেমন লাল দেখায় তার চেয়েও লাল। সব তেজের যেন ওই চোখের মধ্যেই প্রকাশ। সেই লাল চোখদুটি নেশায় ঢুলু ঢুলু করত সর্বক্ষণ। ঠিক যেন মহাকালের অবতার। লোকেরা তাই ভয়ে ভক্তি করত সকলে। বলত, “বাবা রে! সাক্ষাৎ কালভৈরব গো।”
আচার্যিকে দেখলে ভয়ে বুক শুকিয়ে যেত সকলের। শুধু ভয়ের জন্য নয়, গুণের জন্যও ভক্তি করত সবাই।
জিন আর করিমের মতো অপদেবতাও হার মানত আচার্যির কাছে। যাদের হার মানাতে আচ্ছা আচ্ছা গুনিনও হিমশিম খেয়ে যেত। লোকে তাই দুপুর রাতে মাঠে-ঘাটে একলা গেলে নাম নিত আচার্যির। তাদের মনে এ বিশ্বাস স্থিরভাবে জন্মেছিল যে, আচার্যির নাম নিলে ভূত তো ভূত, ভূতের বাবাও আর কাছে ঘেঁষবে না।
সেবারে নাড়ুগ্রামে কলেরা মহামারীরূপে দেখা দিল। গ্রাম উজাড় করে মরতে লাগল সব। যে বাড়িতে রোগ ঢোকে সে বাড়িতে বাতি দিতে কেউ অবশিষ্ট থাকে না। কে কার মুখে জল দেয় এমন অবস্থা!
সবাই গিয়ে তখন লক্ষ্মী আচার্যিকে ধরল।
আচার্যি তখন সবে তাঁর গৃহদেবতা মহাকালীর পুজো সেরে উঠেছেন। উঠেই দেখেন সারি সারি সব দাঁড়িয়ে আছে। বললেন, “কী ব্যাপার রে? আমার এখানে কেন?” লোকো দুলে বলল, “এখন আপনিই আমাদের ভরসা আচার্যি! আপনি দয়া না করলে যে সবাই মারা পড়ি।”
আচার্যি বললেন, “হুঁ।” বলেই একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন। তারপর বললেন, “দেখি মাকে বলে কী করতে পারি! পাপ করবি তোরা, আর মায়ের কাছে হত্যে দেব আমি?”
পঞ্চা বাগদি বলল, “আপনিই আমাদের মা-বাপ। আমাদের হয়ে মাকে আপনিই একটু বলুন। আমাদের ডাক তো মা শুনবে না। আপনার কথা যদি শোনে।”
আচার্যি বললেন, “অমাবস্যা কবে?”
“আজ্ঞে, তা আমরা কি জানি? মুখ্যুসুখ্যু মানুষ।”
আচার্যি তখন হিসেব করে বললেন, “কুজবারে অমাবস্যা আগামীকাল। তোরা শ্মশানে মায়ের পুজোর ব্যবস্থা কর।”
সকলে মহা ধুমধামে হরারডাঙার চটানে শ্মশান-কালীর কাছে পুজোর আয়োজন করল। আচার্যি এলেন পুজো করতে। তবে ভূতের কাঁধে চেপে নয়, হেঁটে হেঁটে। সারারাত ধরে চলল পুজো, হোম ইত্যাদি।
শেষরাতে পুজো শেষ হলে ‘মা মা’ বলে চিৎকার করতে লাগলেন আচার্যি। একটা হাত শূন্যে তুলে বললেন, “দে দে, তাড়াতাড়ি দে।” কার উদ্দেশে কাকে যে বললেন তা কে জানে!
সবাই অবাক হয়ে দেখল, সেই অন্ধকার শ্মশানে মস্ত একটা অর্জুন গাছের ডাল দুলে উঠল। তারপর কালো ছায়ার মতো আধপোড়া একটা হাত আচার্যির হাতে একটা মড়ার মাথার খুলি বসিয়ে দিল।
আচার্যি সেটা নিয়ে মুখের কাছে এনে অনেকক্ষণ ধরে বিড়বিড় করে কীসব মন্ত্রপাঠ করলেন। তারপর সেটা কারণ-মিশ্রিত করে তুলে দিলেন গাঁয়ের লোকেদের হাতে। বললেন, “এই হল মহৌষধ। প্রত্যেকে একবিন্দু করে জিভে দাও। আর যার যার বাড়িতে রোগী আছে তারা সেই রোগীর মুখেও একবিন্দু করে এই ওষুধ দিয়ে দাও।” তারপর বললেন, “তোমরা এখুনি কেউ যাবে না। আমি না যাওয়া পর্যন্ত। এখনও আমার কাজ বাকি আছে।” এই বলে একটা বড় ঝাঁটা হাতে নিয়ে সেই অর্জুন গাছের দিকে তাকিয়ে বললেন, “ওরে কে আছিস?”
গাছের ডাল অমনি দুলে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ছরছর করে একটা ডাল পাতা জোরে নাড়িয়ে দেওয়ার শব্দ।
আচার্যি বললেন, “এই ঝাঁটা নে। মায়ের আদেশ। গ্রাম থেকে ঝেঁটিয়ে সব রোগ এখুনি তাড়িয়ে দে। বুঝলি?”
আবার সেই ভয়ঙ্কর আধপোড়া লম্বা হাত চোখের পলকে আচার্যির হাত থেকে ঝাঁটাটা তুলে নিল।
আচার্যি বললেন, “এবার আমি যাব।” বলে একটা শাঁখ হাতে নিয়ে জোরে ফুঁ দিতে দিতে খালের পাড় ধরে বরাবর চলে গেলেন আচার্যি।
আশ্চর্যের কথা! এরপর কলেরা একদম নির্মূল হয়ে গেল গ্রাম থেকে। আর কেউ মরল না। যারা ভুগছিল তারাও সেরে উঠল। আচার্যির কৃপায় প্রাণে বাঁচল সবাই। সেই থেকে আজ পর্যন্ত নাড়ুগ্রামে আর কখনও কারও কলেরা হয়নি।
লক্ষ্মী আচার্যির ভাই গোবর্ধন আচার্যি একবার বিয়েবাড়ির নেমন্তন্ন খেয়ে দূর গ্রাম থেকে আসছে। তখন মধ্যরাত্রি। ঘুটঘুট করছে অন্ধকার। হালদার পুকুরের পাড়ে এসে বাধা পেল গোবর্ধন। দেখল তার ঠিক যাওয়ার পথটির ওপর বসে আছেন প্রভু। ভয়ে বুক শুকিয়ে গেল গোবর্ধনের। অথচ যাওয়ার এই একটিই মাত্র পথ।
গোবর্ধন তখন অনুনয় বিনয় করতে লাগল, “পথ ছাড়ুন গো মশায়। যেতে দিন।”
কিন্তু কে কার কথা শোনে!
উত্তর এল, “তোর হাতে কী?”
“বিয়েবাড়ি খেতে গিয়েছিলুম। লুচি মিষ্টি মাছ এসব আছে।”
“ওগুলো রেখে যা।
“আজ্ঞে, আমার দাদা লক্ষ্মী আচার্যির জন্য নিয়ে যাচ্ছি।”
“সে তো এখন শ্মশানে বসে জপ করছে। সে খাবে না। তুই রেখে যা।” “কিন্তু দাদার নিষেধ। দাদা যে বলেছে রাতভিতে পথে কেউ কিছু চাইলে দিবি না।” “বলুক। আমার খিদে পেয়েছে। তুই আমায় দে।”
“দেব। তবে তার আগে তুমি আমাকে শ্মশানে দাদার কাছে পৌঁছে দাও। তাকে জিজ্ঞেস করে তারপর দেব।”
ব্যস, কেউ আর নেই। পথ ফাঁকা।
গোবর্ধন মনের আনন্দে পুকুরপাড় থেকে আলে নামল। তারপর আল পেরিয়ে কুলিতে উঠতে যাবে এমন সময় দেখল মস্ত একটা বাঁশঝাড় সটান শুয়ে আছে রাস্তার ওপর। মহা বিপত্তি! কোনওরকমেই যাওয়ার উপায় নেই। গোবর্ধন বলল, “আবার আমার পিছু নিয়েছিস?”
“তুই খাবার দিলি না যে?”
“বললুম তো আমাকে দাদার কাছে নিয়ে চল।”
“তোর দাদার সঙ্গে আমার বিবাদ। তার কাছে যাব না।”
“তবে পথ ছাড়।”
“যা না তুই।”
“কী করে যাব? রাস্তার ওপর এভাবে বাঁশঝাড় শুইয়ে রাখলে কখনও মানুষ যেতে পারে?”
“ও তো ঝড়ে পড়ে গেছে।”
“কোথায় ঝড়? আজ সারাদিন ধরে অসহ্য গুমোট চলছে। পাতা নড়েনি গাছপালার। আর তুই বলছিস ঝড়ে পড়েছে। ওঠ শিগগির।”
“ওর তলা দিয়ে গলে যা না তুই।”
“তা হলে আমাকে টিপে মারবার খুব সুবিধে হয়, না?”
“না রে। কিছু করব না। তোর ভয় করে তুই ডিঙিয়ে যা।”
“তাও যাব না। পথ পরিষ্কার না করলে যাবই না আমি। সকাল হোক। তারপর দাদাকে গিয়ে বলি সব।”
গোবর্ধন আর অনুরোধ না করে বসে পড়ল সেখানে। বসে বসে মা মহাকালী আর লক্ষ্মী আচার্যিকে স্মরণ করতে লাগল।
এমন সময় হঠাৎ গোবর্ধন দেখতে পেল হরারডাঙার দিক থেকে দুটো কঙ্কাল লম্বা লম্বা পা ফেলে এদিকে আসছে। দেখেই তো বুক শুকিয়ে গেল গোবর্ধনের। ভয়ে থরথর করে কাঁপতে লাগল গোবর্ধন। মনে হল, এখুনি হার্টফেল করবে বুঝি।
কঙ্কাল দুটো এসে বলল, “ভয় নেই। আমাদের আচার্যি পাঠিয়েছে।” বলে সেই গাছের দিকে তাকিয়ে বলল, “বড্ড সাহস তোর না? আচার্যি আজ বারোটা বাজাবে তোর। শিগগির গাছ তোল। তারপর আমরাও মজা দেখাচ্ছি তোকে।”
সশব্দে সেই লম্বা লম্বা বাঁশঝাড়গুলো খাড়া হয়ে গেল তখন।
গোবর্ধন আর কোনওদিকে না তাকিয়ে সোজা দৌড় দিল ঘরের দিকে। পেছনে তখন বাঁশঝাড়ের ভেতর তিন ভূতের প্রচণ্ড ধস্তাধস্তি। আর তার সঙ্গে আঁউ আঁউ আর খ্যা খ্যা শব্দ কানে এল।
আলাদপুরের একটা লোককে ভূতে ধরল একবার।
ভূট্টা ভারী বেয়াড়া। সব ওঝা হার মানল তার কাছে। সেখানকার লোকেরা তখন ঠিক করল লক্ষ্মী আচার্যিকে ডাকতে যাবে। গ্রামের বেশ মাতব্বর গোছের দু’জন লোক এসে হাজির হল লক্ষ্মী আচার্যির কাছে।
আচার্যি তাদের চিনতেন। একজনের নাম ভজহরি বিশ্বাস, আর একজনের নাম কেষ্ট দাশ।
আচার্যি বললেন, “কী ব্যাপার ভজহরি! এমন অসময়ে?”
“মুশকিল হয়েছে আচার্যিমশাই।”
“কেন? কেন?”
“আমাদের গ্রামে একজনকে ভূতে ধরেছে। বড় বেয়াড়া ভূত। কিছুতেই ছাড়তে চাইছে না। সব রোজা হার মেনেছে তার কাছে। এখন একমাত্র ভরসা আপনি। আপনি গিয়ে না ছাড়ালে মারা পড়ে যাবে বেচারি।”
“তা না হয় ছাড়াব। কিন্তু যত ভূতে কি তোদেরকেই ধরে? কই, আমাকে তো ধরে না?” “কী যে বলেন আচার্যি! আপনি হলেন গুনিনের সেরা গুনিন। ভূতেরা আপনাকে কাঁধে নিয়ে ঘোরে। আপনার আজ্ঞাবহ। আমাদের ভাগ্য যে আপনার মতো লোককে আমরা বিপদে পাই।”
আচার্যি হেসে বললেন, “চল চল। দেখি কীরকম ভূত ধরেছে তোদের লোককে! খুব তালে এসে পড়েছিস। নাহলে আর একটু পরেই আমি বেরিয়ে যেতাম।” আচার্যি চললেন আলাদপুরে।
আলাদপুরে পৌঁছনোমাত্রই গাঁয়ের উৎসাহী লোকেরা সবাই চলল আচার্যির পিছু পিছু। গুনিনের সেরা গুনিন এসেছে। তাঁর ভূত ছাড়ানো দেখতে হবে বইকী!
খবর পেয়ে আশপাশের গ্রাম থেকেও বহু লোক ছুটল।
আচার্যির ডাক পড়েছে যখন, ব্যাপারটা তখন নিশ্চয়ই সাংঘাতিক।
আচার্যি রোগী দেখলেন। রোগীর চোখমুখের ভাব দেখে বললেন, “হুঁ।” এই হুঁ বলাটা আচার্যির বৈশিষ্ট্য। কোনও জটিলতা দেখলেই হুঁ। তা হলেই লোকেরা বুঝে নেবে অবস্থা গুরুতর। হুঁ বলে আচার্যি বললেন, “দাও দুটি সরষে চোঁয়া আর গুটিকতক প্যাঁকাটি দাও।” রোগীর বাড়ির লোকেরা সঙ্গে সঙ্গে সরষে চুঁইয়ে প্যাঁকাটি ভেঙে আচার্যিকে এগিয়ে দিল। আচার্যি ভৈরবের মতো দাঁড়িয়ে মন্ত্র বলে সেই সরষে চোঁয়া ছুড়ে দিলেন রোগীর গায়ে। আর যায় কোথা! রোগী তখন ‘বাবা রে মা রে।
তারপর প্যাঁকাটির মাথায় আগুন ধরিয়ে সেই আগুন নিভিয়ে পেছনের ফুটোয় ফুঁ দিয়ে মুখে ধোঁয়া দিলেন আচার্যি।
রোগী তো কাটা ছাগলের মতো ধড়ফড় করতে লাগল তখন, “ওরে তোর দুটি পায়ে পড়ি, আমায় অমন করিস না রে! আমি এক্ষুনি ওকে ছেড়ে যাচ্ছি।”
আচার্যি বললেন, “তা তো যাবি রে ব্যাটা। কিন্তু ধরেছিলি কেন?”
আর কথা নেই। ভূতে পাওয়া রোগী একদম চুপ। কেবল গোঁ গোঁ করে। আচার্যি বলেন, “কই রে! কী হল? বল, ওকে ধরেছিলি কেন?”
“ও কেন আমার গায়ে মাছধোয়ার জল ছুড়ে দিয়েছিল?”
“তুই ছিলিস কোথায়?”
“আমি ওদের ছাঁচতলাতে দাঁড়িয়ে ছিলুম।”
“কেন তুই ওদের ছাঁচতলাতে ছিলিস? ও কি ইচ্ছে করে তোকে দেখে তোর গায়ে ফেলেছে?”
“না। আমাকে সরে যেতে না বলে ফেলেছে কেন?”
“বেশ করেছে ফেলেছে। তা তুই যখন দেখলি ও জল ফেলতে আসছে তখন তুই-ই বা সরে গেলি না কেন?”
“বা রে! আমি কি ওকে দেখেছি?”
“ওদের ছাঁচতলায় দাঁড়িয়ে তুই ওকে দেখতে পেলি না, আর ও তোকে না দেখতে পেয়ে তোর গায়ে জল ফেলেছে বলে তুই ওকে ধরলি?”
রোগী তখন প্যাঁচে পড়ে চুপ করে যায়।
আচার্যি বললেন, “তার মানে, ইচ্ছে করে ওকে ধরবি বলেই ওর জল তুই গা পেতে নিয়েছিস?”
“না, তা কেন?”
আচার্যি গম্ভীর গলায় বললেন, “কোথায় থাকিস তুই?”
“মজুমদারার ঈশান কোণে।”
“এই গ্রামের কাছাকাছি আমি থাকি, তুই জানতিস না?”
“জানতুম।”
“তা হলে কেন ধরেছিস বল?”
“তোর গ্রামের লোককে তো ধরিনি আচার্যি।”
“ওরে ব্যাটা। যাক, তুই একে ছাড়বি কিনা বল?”
‘ছেড়ে দেব। সত্যি ছেড়ে দেব।”
“ছেড়ে দেব নয়। এক্ষুনি ছাড়।”
“তুই আগে চলে যা, তারপর ছাড়ছি।”
“না, তোকে এক্ষুনি ছাড়তে হবে।”
“এক্ষুনি?” “হ্যাঁ।”
অবাক কাণ্ড ! যে লোক একটু আগেও ধুলোয় শুয়ে ছটফট করছিল, সে আবার সুস্থ হয়ে আচার্যিকে প্রণাম করে উঠে বসল।
সকলে জয়ধ্বনি করল আচার্যির। বলল, “হুঁ হুঁ বাবা। এ কি যা-তা লোক!” “মনে করো ভূতে আচার্যির পালকি বয়। কত ভূত জব্দ হল—তো এ ব্যাটা কোন ছার।” ভাই।” বলে যে যার চলে গেল।
“আচার্যিও নিজের পাওনাগণ্ডা বুঝে নিয়ে সন্ধের পর ভূতের কাঁধে চেপে ফিরে এলেন। পরের দিন সকালে আলাদপুরের লোকেরা আবার এসে হাজির। সেই ভজহরি বিশ্বাস, বলল, “পেন্নাম হই আচার্যিমশাই।”
ওঃ। এ যে ভেলকি দেখলুম রে
কেষ্ট দাশ আবার এল। এসে হাতজোড় করে আচার্যি তখন দাওয়ায় বসে গঞ্জিকা সেবন করছিলেন। বললেন, “কী ব্যাপার হে? আবার কী মনে করে?”
“ব্যাপার সাংঘাতিক আচার্যিমশাই। আপনি চলে আসার পরই ভূতটা আবার এসে ধরেছে রোগীকে।”
গঞ্জিকার কলকেটা রেখে দিয়ে লাল রক্তজবার মতো চোখ দুটো পাকিয়ে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালেন আচার্যি, “আবার এসেছে? এতবড় স্পর্ধা!”
রাগে উত্তেজনায় আচার্যি ঠকঠক করে কাঁপতে লাগলেন! রাগলে তাঁকে ভয়ঙ্কর দেখায়। আস্ত মানুষটাই যেন পালটে যায় অদ্ভুতভাবে। মুখখানি কঠিন হয়ে ওঠে। গালে ভাঁজ পড়ে। কপাল কুঁচকে যায়। দারুণ দেখায়। আচার্যি বললেন, “ঠিক আছে। আমি যাচ্ছি।”
কিন্তু গেলে কী হবে? তাঁকে আসতে দেখেই ভূতটা ছেড়ে পালাল।
রোগী তখন আবার সুস্থ দেহে প্রণাম করল তাঁকে। বলল, “কী হবে আচার্যিমশাই?” “কিচ্ছু হবে না। কোনও ভয় নেই। আমি তো আছি।”
আচার্যিমশাই চলে গেলেই ভূতটা ভর করে লোকটিকে। আর তাঁকে আসতে দেখলেই ছেড়ে পালিয়ে যায়।
মহা মুশকিল!
আচার্যি ভূতের ঠ্যাটামো দেখে চটে যান। যাবেন নাই বা কেন? এসব ঝামেলা আর ভাল লাগে না তাঁর। খুব কম করেও আশির ওপর বয়স তো হল। মন্ত্রশক্তিতে ভূতকে তিনি বশ করেছেন। কিন্তু জরা মৃত্যুকে জয় করবেন কী করে? এ বয়সে কি আর ভূতের সঙ্গে ছ্যাঁচড়ামো করতে ভাল লাগে কারও? শেষে একদিন রেগে বললেন, “ঠিক আছে। আজ একটা হেস্তনেস্ত করবই এর।” তারপর রোগীর বাড়ির লোকদের বললেন, “দেখ, আজ আর আমি যাব না। তবে কাল তোরা কেউ যেন ডাকতে আসিস না আমাকে। আমি রোজ যে সময়ে যাই কাল তার চেয়ে আগেই আমি যাব। আর আমি গেলে কেউ যেন ব্যস্ত হোস না। কারণ আমি যে গেছি এ-কথাটা রোগী যেন কোনওরকমে জানতে না পারে। কাল একটা শেষ বোঝাপড়া করতে চাই আমি।”
ভজহরি ও কেষ্ট দাশ ফিরে এল।
পরদিন লক্ষ্মী আচার্যি ঠিক দুপুরবেলায় চললেন ভূত ছাড়াতে। আলাদপুরে পৌঁছেই আচার্যি করলেন কি, সর্বাগ্রে একমুঠো ধুলো পড়ে সেই বাড়িটার চারপাশে গণ্ডি দিয়ে দিলেন। তারপর সোজা গিয়ে ঢুকলেন রোগীর ঘরে। রোগী তো আচার্যিকে দেখেই আঁতকে উঠল।
তার পেটের পিলে মাথায় উঠে গেছে তখন। এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে ধরা পড়ে গিয়ে হাউমাউ করে উঠল সে। কিন্তু সে মাত্র ক্ষণিকের জন্য। পরক্ষণেই আবার স্বাভাবিক হয়ে গেল।
রোগী আবার সুস্থ হয়ে প্রণাম করল আচার্যিকে। অতি কষ্টে চিঁ চিঁ করে বলল, “মরে গেলুম আচার্যিমশাই। আর তো পারি না। এইমাত্র আপনাকে দেখে আমাকে ছেড়েছে। আপনি চলে গেলেই আবার ধরবে আমায়।”
আচার্যি বললেন, “চুপ করে বসে থাকো তুমি। ওর যাওয়ার রাস্তা আমি বন্ধ করে দিয়ে এসেছি। আবার এক্ষুনি এসে ধরবে ও তোমাকে।”
আচার্যির কথা শেষ হতে না হতেই চেঁচিয়ে উঠল রোগী। চোখ লাল করে বলল, “ধরবে না তো কী করবে শুনি? এত লোকের ওলাউঠো হয়, তোর হয় না? তোর কী এমন পাকা ধানে মই দিয়েছি আমি যে, আমাকে তাড়াবার জন্য এমন উঠেপড়ে লেগেছিস?”
আচার্যি বজ্রগম্ভীর স্বরে বললেন, “ওকে তুই ছেড়ে দিয়ে আবার কেন ধরেছিস বল?” “কেন ধরব না! আমি তো চলেই যাচ্ছিলাম। কেন তুই গণ্ডি দিলি?”
“আজ তোর শ্রাদ্ধ করব বলে গণ্ডি দিয়েছি।”
রোগী নিজের মনে বিড়বিড় করে কী যেন বলল। হয়তো বা গালাগালি করল আচার্যিকে।
আচার্যি রোগীকে বললেন, “তুই যে সেদিন বললি আমি ওকে ছেড়ে যাব, তা আবার কেন ধরলি?”
আর কোনও উত্তর নেই রোগীর মুখে।
আচার্যি এবার তাঁর ঝোলার ভেতর থেকে একটা মড়ার মাথার খুলি বের করলেন।
খুলিটা দেখেই লাফিয়ে উঠল রোগী, “ওরে বাবা। ওটা তুই বের করলি কেন আচার্যি? শিবু চাঁড়ালের জামাই বিশুর করোটি ওটা, ও যে আমি চিনি। বিশুকে সাপে কাটল সেবার রথের দিনে। তা সে মড়া কেউ পোড়াতে দিল না। গাঁয়ের লোকেরা বলল কলার মাঞ্জাসে করে ওটা খালের জলে ভাসিয়ে দাও। সেই মড়া বাবুর মায়ের খালে ভেসে ঠেকল গিয়ে হরারডাঙার চটানে। শেয়াল কুকুরে ছেঁড়াছিঁড়ি করল। মাথাটা নিয়ে তুই প্রেতপুজো করে পচালি। তারপর তোর চ্যালারা ওটা পরিষ্কার করে তোকে কারণ খেতে দিল। ওটা তোর ঝুলিতে রেখে দে আচার্যি। তোর পায়ে পড়ি।”
আচার্যি তখন ঝুলির ভেতর থেকে একটা বোতল বের করলেন। বললেন, “দেখছিস তো?”
“ওতে কী রে আচার্যি?”
“স্বাতী নক্ষত্রের জল।’
আচার্যি মড়ার মাথার খুলিতে স্বাতী নক্ষত্রের জল ঢেলে অনেকক্ষণ ধরে বিড়বিড় করে কীসব মন্ত্র পড়লেন। তারপর সেই জল ছুড়ে মারলেন রোগীর গায়ে। রোগী তখন ‘বাপ রে মা রে’ করে উঠল।
“ওরে আমার ঘাট হয়েছে রে। তোর পায়ে পড়ি আচার্যি। আমায় ছেড়ে দে। আর ধরব না একে।”
‘তোকে আজ ঝাঁটাপেটা করে তাড়াব আমি।”
রোগী এবার তেতে উঠল, “দ্যাখ আচার্যি, মুখ সামলে কথা বলবি। আমাকে তুই যা-তা মনে করিসনি। এককালে আমি মস্ত পণ্ডিত ছিলুম। আজ কর্মদোষে প্রেতযোনি পেয়েছি তাই। যা বললি তা আর কোনওদিন বলবি না।”
“বেশ করব, বলব। যে সত্যিকারের পণ্ডিত হয় সে কখনও এইরকম ছ্যাঁচড়ামো করে ?”
“খবরদার বলছি, আমার সঙ্গে সমীহ করে কথা বলবি।”
“বেশ, বলব। তুই সত্যিই পণ্ডিত কি আকাট মুখ্যু তার পরিচয় দে আগে। তারপর বলব।”
“ঠিক আছে। আমাকে তুই পরীক্ষা কর।”
আচার্যি একটু সময় কী যেন ভাবলেন। তারপর বললেন, “বল দেখি হরধনু ভেঙেছিল?”
“তোর মরা বাবা ভেঙেছিল। ওই নাম আমাকে বলতে আছে যে বলব?”
“তুই ব্যাটা জানিস যে বলবি?”
“জানি না তো জানি না। আমায় এবারের মতো ছেড়ে দে। আমার ঘাট হয়েছে।”
“এখন কি ছাড়ব? আগে তুই স্বীকার কর যে, তুই মুখ্যু। তবে তো ছাড়ব।”
“তা কেন করব?”
“তবে কেন ছাড়ব?”
“ওই প্রশ্নটা বাদ দিয়ে অন্য প্রশ্ন কর তুই।”
আচার্যি বললেন, “বেশ, তাই করছি। বল, দশরথের বড়ছেলের নাম কী?” “বলব না। ও নাম আমাকে বলতে নেই।”
“না বললে আমিও ছাড়ব না। আরও গালাগালি দেব।”
“একান্তই বলাবি তা হলে?”
“হ্যাঁ।”
“তবে শোন, সীতার পতির যে নাম, দশরথের বড়ছেলের সেই নাম।”
‘এরকম উত্তর তো আমি চাই না।”
“আর আমাকে জ্বালাস না আচার্যি। ওই নাম বললেই আমি উদ্ধার হয়ে যাব। আমি তিন সত্যি করছি, আর কখনও এর ত্রিসীমানায় আসব না। এবার আমায় ছেড়ে দে।” “যা। দূর হয়ে যা। তবে তুই যে যাচ্ছিস তার একটা চিহ্ন দিয়ে যা।”
“কী চিহ্ন চাস তুই বল?”
“এই শিলটাকে মুখে করে নিয়ে যা।”
“ওরে বাবা! ও আমি পারব না। আমার শরীর বড় দুর্বল। আমায় অন্য কিছু করতে বল আচার্যি।”
“তবে ওই জুতোজোড়াটা নিয়ে যা।”
“জুতো আমি ছুঁই না।”
“বেশ। ওই পাকুড়গাছের একটা কাঁচা ডাল ভেঙে দিয়ে যা তবে।”
“তা যাচ্ছি। গণ্ডি মুছে দে।”
আচার্যি গণ্ডি কেটে দিলেন।
তারপর সকলকে বললেন, “পাকুড়গাছের ডালটা ভাঙামাত্রই তারা যেন রোগীকে ধরে ফেলে। কেননা ভূতে ধরা লোকের গা থেকে ভূত যদি ছেড়ে যায় তবে সে-সময় পড়ে গেলে হয় অঙ্গহানি, নাহলে মৃত্যু হতে পারে। রোজার বাবারও তখন আর করবার কিছু থাকে না।” যা হোক, রোগী তখন মাতালের মতো টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল।
তারপর সেইভাবেই টলতে টলতে কুলি (রাস্তা) ধরে পাকুড়গাছটার দিকে চলল। রোগীর সঙ্গে চলল কয়েকজন সদাসতর্ক লোক।
পাকুড়তলায় যাওয়ামাত্রই বিরাট একট কাঁচা ডাল সকলের জোড়া জোড়া চোখকে বিস্মিত করে মড়মড় শব্দে ভেঙে পড়ল গাছতলায়। আর সেইসঙ্গে হু হু করে হাওয়া বইতে লাগল। সে কী ভীষণ দমকা হাওয়া। যেন ঝড় উঠল। ধুলো কুটো শূন্যে উঠে ঘুরপাক খেতে লাগল।
সঙ্গে সঙ্গে রোগীর বাড়ির লোকেরা ধরে ফেলল রোগীকে। তারপর সবাই মিলে ধরাধরি করে ধরে নিয়ে এল তাকে।
আচার্যি একটা রক্ষাকবচ করে ঝুলিয়ে দিলেন তার গলায়। আচার্যির কৃপায় সে-যাত্রা বেঁচে গেল লোকটি।
লক্ষ্মী আচার্যির ধন্য ধন্য পড়ে গেল চারদিকে। হ্যাঁ, গুনিনের মতো গুনিন বটে! সবার সেরা গুনিন।
শুধু এই ঘটনা নয়—
আরও বহু ঘটনায় সাফল্য লাভ করেছেন লক্ষ্মী আচার্যি।
তবে কেউ প্রশংসা করলে তিনি খেপে যেতেন। বলতেন, “বেরো শালারা। যা করেছে তা আমার মা ব্রহ্মময়ী করেছে। আমি কী করেছি রে! আমায় তোষামোদ করতে এসেছিস কেন? মায়ের চেয়ে আমি বড়, না?”
কাজেই আচার্যির কাছে কেউ বড় একটা বিপদে না পড়লে সচরাচর যেত না। আচার্যি গুনিন মানুষ তো। দিনরাত নেশায় চুর হয়ে থাকতেন। সন্ধে হলেই ভূতের কাঁধে চেপে যেতেন হরারডাঙায়। হরিহরডাঙার চটানে।
সেখানে একদল ভূত এসে জমত।
কালো কালো ছায়া ছায়া ভূতেরা, আলোর রেখার মতো কঙ্কালের দল ঝুপঝাপ করে গাছের ডাল থেকে নেমে আসত।
শ্মশানের শ থেকে উঠে আসত কায়াহীন ছায়ারা।
আচার্যি গাঁজার কলকেটা এগিয়ে দিয়ে বলতেন, “এটা ঠিক করে সেজে দে।”
অমনি একজন সেটা হাত নিয়ে সাজতে বসত। শ থেকে ফুঁ দিয়ে আগুন বের করে ধরাত। তারপর বলত, “এই নে খা। একটু পেসাদ আমাদেরকেও দিস আচার্যি।” আচার্যি একটা টান দিয়ে ভূতদের হাতে তুলে দিতেন সেই কলকেটা। তারপর সেটা হাতে হাতে ঘুরত।
আড়ালে আবডালে লুকিয়ে এ দৃশ্য যারা দেখত তারা এসে গল্প করত অন্যদের কাছে। সকলে অবাক হয়ে যেত শুনে। চোখদুটো বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে উঠত।
পেঁচোয় পেয়েছে একটা ছেলেকে। কখনও নীল, কখনও লাল হয়ে যাচ্ছে। সবাই বলল, “ও ছেলে বাঁচবে না। চারদিনের ছেলে। বাঁচে কখনও?” খবর গেল আচার্যির কাছে।
বললেন, “বাঁচবে না মানে? আমি বাঁচাব ওকে।”
সবাই কেঁদেকেটে পায়ে ধরল আচার্যির, “দয়া করুন আচার্যিমশাই।”
“দয়া তো করছি রে বাবা। বলছি তো বাঁচাব। আজ মাঝরাতে ছেলের মাকে একলা যেতে বলবি শ্মশানে। ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে যাবে শুধু। তারপর আমি আছি।”
“একলা যাবে? ভয় করবে না বাবা?”
“ভয় করলে তো চলবে না। ছেলেকে বাঁচাতে গেলে সাহস করে যেতে হবে।” যেতে যখন হবেই তখন যাওয়া হল।
ছেলেকে বুকে নিয়ে ছেলের মা একলা চলল হরারডাঙার চটানে!
বাবুর মায়ের খালের ধারে আসতেই কে যেন বলল, “তুই ওইখানেই বোস মা। ছেলেটা দে।”
ছেলের মা খালের ধারে বসে পড়ল।
“দে। ছেলেটা দে।”
ছেলের মা তো অবাক! কাউকেই তো সে দেখতে পাচ্ছে না। দেবে কাকে? “ছেলেটাকে তুলে ধর। আমি নিয়ে নিচ্ছি।”
ছেলেকে তুলে ধরল মা।
অমনি কোথা থেকে দুটো হাত এসে নিয়ে নিল ছেলেটিকে।
লক্ষ্মী আচার্যি শ্মশানে ছিলেন।
সেই হাতদুটো ছেলেটাকে নিয়ে আচার্যির পায়ের কাছে নামিয়ে রাখল।
আচার্যি বললেন, “এখানে রাখলি কেন, শ-এর ওপর শুইয়ে দিয়ে আয়।”
অমনি পেছন থেকে ছেলের মা কেঁদে উঠে বলল, “না না। আঁতুড়ের ছেলে। ওকে শ-এ শোয়াবেন না আচার্যিমশাই। কচি গা। বড্ড লাগবে।”
আচার্যি গম্ভীর গলায় বললেন, “তুই এখানে এলি কেন? তোকে না খালের ধারে বসতে বললাম।’ “
“ক্ষমা করুন আমাকে! আমি থাকতে পারলুম না।”
বোস। কথা বলবি না। উঠবি না।” তারপর কাকে যেন উদ্দেশ্য করে বললেন, “কই রে! যা, শ-এর ওপর রেখে আয় ওকে।” অমনি সেই হাতদুটো ছেলেটাকে তুলে নিয়ে রেখে এল শ-এর ওপর। ছেলে তো নয়, লাল রক্তমাংসের ড্যালা একটি। কখনও লাল, কখনও নীল, কখনও হলুদ হয়ে যাচ্ছে ছেলেটার গায়ের রং।
আচার্যি বললেন, “ঠিক আছে। এসেছিস যখন,
ছেলের মা অধীর আগ্রহে বসে রইল।
রাত যখন শেষ হয়ে আসছে, আচার্যি তখন ছেলের মাকে বললেন, “যা। এবার তোর ছেলে নিয়ে তুই ঘরে চলে যা।”
মা তো আনন্দে লাফিয়ে উঠল।
“উঁহুঁ। উঠো না। বোসো।” বলে শ–এর দিকে তাকিয়ে ছেলেটাকে ডাকলেন তিনি, “আয়। উঠে আয়।”
মা তো অবাক! চারদিনের ছেলে উঠে আসবে কী! কিন্তু উঠে এল ছেলেটি।
আচার্যির ভেলকিতে সবকিছুই সম্ভব হয়।
চারদিনের ছেলে পা পা করে এগিয়ে এসে মায়ের কোলে শুয়ে পড়ল।
আচার্যি বললেন, “যাঃ! খুব বেঁচে গেছে এ যাত্রা। আর কোনও ভয় নেই। সাবধানে রাখিস। কাল একটা মাদুলি করে দেব। সেটা ছেলের গলায় পরিয়ে দিবি।”
ছেলের মা ছেলে নিয়ে চলে গেল।
লক্ষ্মী আচার্যির যশের ধারা গড়িয়ে পড়ল দেশ-দেশান্তরে। এইভাবেই দিন যায়।
একদিন আচার্যি যখন হরারডাঙায় যাচ্ছিলেন, পালকি বইতে বইতে ভূতেরা তখন বলল, “আচ্ছা গুনিন—।”
গুনিন তখন নেশায় চুর, “কী রে!”
“আচ্ছা, তুই এত সাহস পেলি কোত্থেকে রে?”
“কেন, আমার মা ব্রহ্মময়ীর কাছ থেকে পেয়েছি।”
“সত্যি গুনিন, তোর মতো সাহসী লোক একজনও দেখিনি আমরা। আচ্ছা, তোর কি কোনও কিছুতেই ভয় করে না? এই যে আমাদের কাঁধে চেপে ঘুরে বেড়াস, হাজার হলেও মানুষ তো তুই?”
“নাঃ। তোরা দেখছি ভূত তো ভূত। ভয় থাকলে কখনও তোদের কাঁধে চেপে ঘুরে বেড়াই?”
“তা বটে। তা বটে।”
“কিন্তু তোদের মতলবটা কি বল তো? আজ হঠাৎ এ কথা জিজ্ঞেস করছিস যে?” “না। মতলব আর কি! হাজার হলেও তুই আমাদের মনিব। তাই জিজ্ঞেস করছিলুম যদি তোর কোনও কিছুতে ভয়ডর থাকে তবে সে ভয়টা আমরা ভেঙে দেব। এই আর কি।”
এই কথা রোজই হয়।
আচার্যি বলেন, “তোরা ব্যাটারা জ্বালিয়ে মারলি। আমার আবার ভয় কী?” ভূতেরা বলে, “বল না গুনিন?”
আচার্যি বলেন, “আমি কাউকে ভয় করি না। কোনও ব্যাটাকে ভয় করি না।” ভূতেরা চুপ করে যায়।
অন্যদিনের মতো সেদিনও সন্ধের পর ভূতেরা আচার্যির পালকি বয়ে আনছিল। আচার্যি সেদিন দারুণ নেশা করেছিলেন।
টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল। তা সত্ত্বেও সেই বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে তিনি শ্মশানে যাচ্ছিলেন জপ করতে।
অন্যদিনের মতো সেদিনও ভূতেরা বলল, “বল না গুনিন, তোর কীসে ভয়?” আচার্যি বললেন, “ভয় আবার কীসের?”
“বল না বাবা?”
নেশায় আরক্ত চোখদুটিকে একবার চারদিকে ঘুরিয়ে আচার্যি বললেন, “একান্তই শুনবি তা হলে?”
“হ্যাঁ, হ্যাঁ। শুনব।”
“ভয় অবশ্য তেমন কিছু নয়। তবে—।”
“তবে? তবে কি? বল না?”
“শ্মশানে নামবার মুখে যে শ্যাওড়া গাছটা আছে, দেখেছিস?”
“হ্যাঁ হ্যাঁ। ওই গাছের ডালে তো শশধর নাপিত গলায় দড়ি দিয়েছিল?”
“হ্যাঁ। ওই শ্যাওড়া গাছের ডাল থেকে একটা হুট্ ট্যাঁটারু পাখি ডেকে ওঠে?” “ডাকে। রোজ ডাকে।”
“ওই পাখিটা যখন আচমকা ডেকে ওঠে তখন কেন জানি না আমার বুকের ভেতরটা ছ্যাঁত করে ওঠে। এই যা। আর কিছু নয়।”
“এঃ হে। এই কথা! তা আমাদের আগে বলিসনি কেন গুনিন। দেখ না আজই ব্যাটাকে শেষ করে দিচ্ছি।”
“দিবি? তাই দে, একেবারে খতম করে দে ব্যাটাকে।”
“সে-কথা আবার বলতে?”
কিছুক্ষণ পরেই হরারডাঙা এসে গেল। আর চরের ঢালে শ্মশানে নামার মুখেই বিপর্যয়টা ঘটে গেল হঠাৎ।
ঘুরঘুট্টি অন্ধকারে বনবাদাড়ের ভেতর থেকে পাখিটা বিকট স্বরে ডেকে উঠল সেদিনও—হু-হু-হুট-ট্যাঁ-ট্যাঁ—।”
চমকে উঠলেন গুনিন।
আর সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, কেউ যেন তাঁর পালকিটাকে দেশলাইয়ের খোলের মতো ছুড়ে ফেলে দিল।
অমনই কোটি কোটি গলায় কারা যেন ভীষণ রবে ডেকে উঠল সেই পাখিটার স্বর নকল করে—হু-হু-হু-ট্যাঁ-ট্যাঁ। হুট্-ট্যাঁ ট্যাঁ। হুট্-ট্যাঁ—
শুধু তারা নয়, আশপাশ থেকে চারদিক থেকে তখন সে কি হাসি। হোঃ হোঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ। আর আর্তনাদ—আঁ-আ-আ। আঁ-আ-আ—।
শ্মশানের শ থেকে যেন হাজার হাজার কায়াহীন ছায়ারা সব এলোমেলো উঠে দাঁড়াল। গুনিন বুঝতে পারলেন আজ আর তাঁর নিস্তার নেই।
নেশার ঘোর কেটে গেছে তখন। বুক ঢিপ ঢিপ করছে ভয়ে। ছিটকে পড়ে গিয়ে সারা গায়ে হাতে কী অসহ্য যন্ত্রণা। কোমরের অস্থিসন্ধিটাও ভেঙে গেল নাকি? বুকটা ভিজে ভিজে ঠেকছে। বোধ হয় নাক দিয়ে রক্ত ঝরছে। আচার্যি দেখতে পেলেন, দুটো আধপোড়া হাত ক্রমশ ধীরে ধীরে তাঁর গলার কাছে এগিয়ে আসছে!