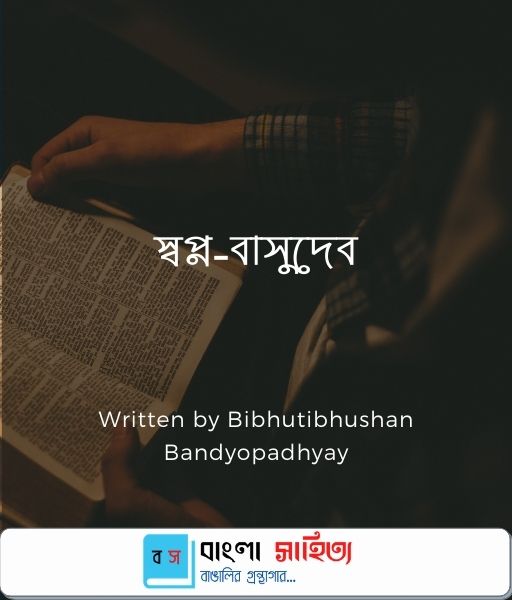পাড়াগাঁয়ের মাইনার স্কুল। মাঝে মাঝে ভিজিট করতে আসি, আর কোথাও থাকবার জায়গা নেই, হেডমাস্টার অবিনাশবাবুর ওখানেই উঠতে হয়। অবিনাশবাবুকে লাগেও ভালো, বছর বিয়াল্লিশ বয়স, একহারা চেহারা, বেশ ভাবুক লোক। বেশি গোলমাল ঝঞ্ঝাট পছন্দ করেন না, কাজেই জীবনের পথে বাধা ঠেলে অগ্রসর না-হতে পেরে দেবলহাটি মাইনার স্কুলের প্রধান শিক্ষকরূপে পনেরো বছর কাটিয়ে দিলেন এবং বাকি পনেরোটা বছর যে এখানেই কাটাবেন তার সম্ভাবনা ষোলো আনার ওপর সতেরো আনা।
কার্তিক মাসের শেষে হেমন্ত সন্ধ্যা। স্কুলের বারান্দাতে ক্লাসরুমের দু-খানা চেয়ার টেনে নিয়ে আমরা গল্প করছিলাম। সামনেই একটা ছোটো মাঠ, একপাশে একটা বড়ো হুঁতগাছ, একপাশে একটা মজা পুকুর। সামনের কাঁচা রাস্তাটা গ্রামের বাজারের দিকে গিয়েছে। স্থানটা নির্জন।
চায়ের কোনো ব্যবস্থা এখানে হওয়া সম্ভব নয়, তা জানি। একটি গরিব ছাত্র হেডমাস্টারের বাসায় থেকে পড়ে আর তাঁর হাটবাজার করে। সে এসে দুটো রেকাবিতে ঘি-মাখানো রুটি, আলুচচ্চড়ি ও একটু গুড় রেখে গেল। আমি বললুম —অবিনাশবাবু, বেশ ঠান্ডা পড়েচেবেশ গরম মুড়ি খাবার ইচ্ছে হচ্ছে, কিন্তু…
—হ্যাঁ, হ্যাঁ—সার্টেনলিওরে ও কানাই, শোন, শোন, যা দিকি একবার গঙ্গার বউয়ের বাড়ি, আমার নাম করে বল গে, দুটি গরম মুড়ি ভেজে দ্যায়—এক্ষুনি…
আমি বললুম, অভাবে চালভাজা…
তারপর গল্পগুজবে আধঘণ্টা কেটে গেল। অবিনাশবাবু কথা বলতে বলতে কেমন অন্যমনস্কভাবে মাঝে মাঝে বাঁ-ধারের মজা পুকুরটার দিকে চাইছিলেন। হঠাৎ বললেন—মুড়ি আসুক, একটা গল্প বলি ততক্ষণ। শুনুন, ইন্সপেক্টারবাবু। এইরকম শীতের সন্ধ্যাতেই কথাটা মনে পড়ে। আপনাকে পেয়ে মনে এত আনন্দ হয়!…এখানকার লোকজন দেখেছেন তো? সব দোকানদার, লেখাপড়ার কোনো চর্চা নেই, ছেলেপিলেকে লেখাপড়া শেখায় এইজন্যে যে কোনরকমে ধারাপাত আর শুভঙ্করীটা শেষ করাতে পারলেই দাঁড়ি ধরাবে। কারুর সঙ্গে কথা বলে সুখ পাইনে, ঝালমসলার দরের কথা কাঁহাতক আলোচনা করি বলুন। ভদ্রঘরের ছেলে,–হয় এসে পড়েচি পেটের দায়ে এই পাণ্ডববর্জিত দেশে, কিন্তু তা বলে মনটা তো—কলেজের দু-চার ক্লাস চোখে দেখেছিলামও তো—পড়াশুনো না-হয় নাই করেচি…
দেখলাম অবিনাশবাবু কলেজের দিনগুলোর কথা এখনও ভুলতে পারেননি। বেচারির জীবনে জাঁকজমক নেই, আত্মপ্রতিষ্ঠার দুরাশা নেই, সাহসও বোধ করি নেই। তাঁর যা-কিছু অভিজ্ঞতা, যা-কিছু কর্মনৈপুণ্য, সবই এই অনাড়ম্বর সরল জীবনধারাকে আশ্রয় করে। কলেজের দিনগুলোতেই শহরের মুখ দেখেছিলেন, আড়ম্বর বা বিলাসিতা—মনেরই বলুন বা দেহেরই বলুন—ওই কলেজের ক-টা বছরেই তার আরম্ভ ও শেষ। সে দিনগুলো যত দূরে গিয়ে পড়চে, রঙিন স্মৃতির প্রলেপ তাদের ওপর যে তত বিচিত্র ও মোহময় হয়ে পড়বে এটা খুব স্বাভাবিক বটে।
অবিনাশবাবু তামাক ধরিয়ে আমার হাতে দিয়ে আবার বলতে শুরু করলেন।
—হুগলি জেলার কোনো এক গ্রামে ছিল আমার বাড়ি।
আমি জিজ্ঞাসা করলাম,—ছিল কেন? এখন নেই?
—সে-কথা পরে বলচি। না, এখন নেই ধরে নিতে পারেন। কেন যে নেই, তার সঙ্গে এই গল্পের একটা সম্বন্ধ আছে, গল্পটা শুনলেই বুঝবেন।
হুগলি জেলার কোনো এক গ্রামে আমার মামারবাড়ি ছিল। ছেলেবেলায় যখন সর্বপ্রথম মায়ের সঙ্গে সেখানে যাই, তখন আমার বয়স বছরপাঁচেক। আমাদের মামারবাড়ির পাড়ায় আট-নয় ঘর ব্রাহ্মণের বাস, ঘেঁষাঘেঁষি বসতি, একচালে আগুন লাগলে পাড়াসুদ্ধ পুড়ে যায়, এমন অবস্থা। কোঠাবাড়ি ছিল কেবল আমার মামাদের, আর সব খড়ের ছাউনি, ছোটো-বড়ো আটচালা ঘর, এপাড়া থেকে ওপাড়া যাবার পথে একটা বড়ো আম-কাঁঠালের বাগান, বনজঙ্গল, সজনে গাছ ও দু-একটা ডোবা। বনজঙ্গলের মধ্যে দিয়ে অনেকদ্দূর গেলে তবে ওপাড়ার প্রথম বাড়িটা। সেই বনজঙ্গলের মধ্যে কাদের একটা কোঠাবাড়ি খানিকটা গাঁথা হচ্চে।
সেবার কিছুদিন থেকে চলে আসবার পর আবার যখন মামারবাড়ি গেলুম, তখন আমার বয়স আট বছর। গ্রামটা অনেক দিন পরে দেখতে বেরিয়ে চোখে পড়ল, এপাড়া-ওপাড়ার মধ্যে বাঁ-দিকে ডোবার ধারের একটা জায়গা। একটু অবাক হয়ে গেলাম। ডোবার পাড়ের জঙ্গল অনেকটা কাটানো, কাদের একটা কোঠাবাড়ি খানিকটা গাঁথা অবস্থায় দাঁড়িয়ে, কিন্তু মনে হল অনেক দিন গাঁথুনির কাজ বন্ধ আছে, যে-জন্যই হোক, কারণ ভিতের গায়ে ও ঘরের মেঝেতে ছোটো-বড়ো ভাঁটশাওড়ার গাছ গজিয়েচে, চুন-সুরকি মাখার ছোটো খানাতে পর্যন্ত বনমুলোর চারা। মনে পড়ল, সেবার এসে বাড়িটা গাঁথা হচ্চে দেখেছিলুম। এখনও গাঁথা শেষ হয়নি তো? কারা বাড়ি তুলচে?
ছুটে গিয়ে দিদিমাকে জিজ্ঞেস করলুম।
—কারা ওখানে বাড়ি করচে দিদিমা, সেবার এসে দেখে গিইচি, এখনও শেষ হয়নি?
—তোর এত কথাও মনে আছে!…ও তোর ভণ্ডুলমামা বাড়ি করছে, এখানে তো থাকে না, তাই দেখাশোনার অভাবে গাঁথুনি এগুচ্চে না।
আমার ভারি কৌতূহল হল, সাগ্রহে বললুম, ভণ্ডুলমামা কোথায় থাকে দিদিমা? ভণ্ডুলমামা কে?…
—ভণ্ডুল রেলে চাকরি করে, লালমণিরহাটে না কোথায়। আমাদের গাঁয়েই ছেলেবেলায় থাকত, বাড়িঘর তো ছিল না। ওপাড়ার মুখুয্যেবাড়ির ভাগনে, চাকরিবাকরি করছে, ছেলেপুলে হয়েছে, একটা আস্তানা তো চাই? তাই টাকা পাঠিয়ে দ্যায়, মুখুয্যেরা মিস্ত্রি লাগিয়ে ঘরদোর শুরু করে দিয়েছে, নিজে ছুটিতে এসে মাঝে মাঝে দেখাশোনা করে—
আমি ছাড়বার পাত্র নই, বললুম,—তবে বাড়ি গাঁথা হচ্ছে না কেন? মুখুয্যেরা তো দেখলেই পারে?
—তা নয়, সবসময় তো টাকা পাঠাতে পারে না? যখন পাঠায়, তখন মিস্ত্রি লাগানো হয়।
কী জানি কেন সেই থেকে এই ভণ্ডুলমামা ও তাঁর আধ-গাঁথা বাড়িটা আমার মনে একটা অদ্ভুত স্থান অধিকার করে রইল। রূপকথার রাজপুত্রের মতোই এই ভণ্ডুলমামা হয়ে রইলেন অবাস্তব, স্পর্শের অতীত, দর্শনের অতীত, এক
মানসরাজ্যের অধিবাসী, তাঁর চাকরির স্থান লালমণিরহাট, মায় তাঁর ছেলে মেয়েসুদ্ধ। তাঁর টাকা পাঠাবার ক্ষমতা বা অক্ষমতাও যেন কোথায় আমার ব্যক্তিগত সহানুভূতির বিষয়ীভূত হয়ে দাঁড়াল, অথচ কেন এসব হল তার কোনো ন্যায়সংগত কারণ আজও মনের মধ্যে খুঁজে পাই না।
কতবার দিদিমাদের চিলেকোঠার ছাদে শুয়ে দিদিমার মুখে রূপকথা শুনতে শুনতে অন্যমনস্ক মনে ভেবেচি—লালমণিরহাট থেকে ভণ্ডুলমামা আবার কবে। টাকা পাঠাবে বাড়ি গাঁথার জন্যে?…না, এবার বোধ হয় নিজে আসবে। মুখুয্যেরা বোধ হয় ভণ্ডুলমামার টাকা চুরি করে, তাই ওদের হাতে আর টাকা দেবে না। ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমির গল্পের ফাঁকে দিদিমাকে কখনো বা জিজ্ঞেস করি—লালমণিরহাট কোথায় দিদিমা? দিদিমা অবাক হয়ে বলেন—লালমণিরহাট! কেন, তাতে তোর হঠাৎ কী দরকার পড়ল?…তা, কী জানি বাপু কোথায় লালমণিরহাট? নে নে, ঘুমুস তো আমায় রেহাই দে,রাত্তিরে এখন গিয়ে আমায় দুটো মোচা কুটে রাখতে হবে, ঠাকুরঘরের বাসন বের করতে হবে, ছিষ্টির কাজ পড়ে রয়েছে—তোমায় নিয়ে সারারাত গল্প করলে তো চলবে না আমার।
আমি অপ্রতিভের সুরে বলতুম—না দিদিমা, গল্প বললো, যেও না, আচ্ছা মন দিয়ে শুনছি।
এর পরে আবার মামারবাড়ি গেলুম বছর দুই পরে। এই দু-বছরের মধ্যে আমি কিন্তু ভণ্ডুলমামার বাড়ির কথা ভুলে যাইনি। শীতের সন্ধ্যায় গোয়ালে সাঁজালের ধোঁয়ায় আমাদের পুকুরপাড়টা ভরে যেত, বনের গাছপালাগুলো যেন অস্পষ্ট, যেন মনে হত সন্ধ্যায় কুয়াশা হয়েছে বুঝি আজ, সেইদিকে চাইলেই আমার অমনি মনে পড়ত ভণ্ডুলমামার সেই আধ-তৈরি কোঠাবাড়িটার কথা—এমনি শ্যাওড়াবনে ঘেরা পুকুরপাড়ে—এতদিনে কতটা গাঁথা হল কে জানে? এতদিন নিশ্চয় ভণ্ডুলমামা মুখুয্যেবাড়ি টাকা পাঠিয়েছে।
মামারবাড়িতে রাতে এসে পৌঁছালাম। সকালে ওই পথে বেড়াতে গিয়ে দেখি–ও মা, এ কী, ভণ্ডুলমামার বাড়িটা যেমন তেমনি পড়ে আছে! চার-পাঁচ বছর আগে যতটা গাঁথা দেখে গিয়েছিলুম, গাঁথুনির কাজ তার বেশি আর একটুও এগোয়নি, বনে-জঙ্গলে একেবারে ভর্তি, ইটের গাঁথুনির ফাঁকে বট-অশ্বথের বড়ো বড়ো চারা। আহা, ভণ্ডুলমামা বোধ হয় টাকা পাঠাতে পারেনি আর!
ভণ্ডুলমামার সম্বন্ধে সেবার অনেক কথা শুনলাম। ভণ্ডুলমামা লালমণিরহাটে নেই, সান্তাহারে বদলি হয়েছে। তার এখন দুই ছেলে, দুই মেয়ে। বড়ো ছেলেটি আমারই বয়সি, ভণ্ডুলমামার মা সম্প্রতি মারা গিয়েচে। বড়ো ছেলেটির পৈতে হবে সামনের চৈত্রমাসে। সেই সময়ে ওরা দেশে আসতে পারে।
কিন্তু সেবার চৈত্রমাসের আগেই দেশে ফিরলুম, ভণ্ডুলমামার সঙ্গে আর যোগাযোগ হয়ে উঠল না।
বছরতিনেক পরে। দোলের সময়। মামারবাড়ির দোলের মেলা খুব বিখ্যাত, নানা-জায়গা থেকে দোকানপসারের আমদানি হয়। আমি মায়ের কাছে আবদার শুরু করলুম, এবার আমি একা রেলে চড়ে মেলা দেখতে যাব মামারবাড়ি। আমায় একা ছেড়ে দিতে বাবার ভয়ানক আপত্তি, অবশেষে অনেক কান্নাকাটির পর তাঁকে রাজি করানো গেল। সারাপথ সে কী আনন্দ! একা টিকিট করে, রেলে চড়ে, মামারবাড়ি চলেছি। জীবনে এই সর্বপ্রথম একা বাড়ির বার হয়েচি সেই আনন্দেই সারাপথ আত্মহারা!
কিন্তু এ সুখ সইল না। মামার বাড়ির স্টেশনে নেমেই কীরকম হোঁচট খেয়ে প্ল্যাটফর্মের কাঁকরের উপর পড়ে গিয়ে আমার হাঁটু ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল। অতিকষ্টে মামার বাড়ি পৌঁছে বিছানা নিলুম। পরদিন সকালে উঠতে গিয়ে দেখি আর উঠতে পারিনে—দুই হাঁটুই বেজায় টাটিয়েছে; সঙ্গে সঙ্গে জ্বর। কোথা দিয়ে দোল কেটে গেল টেরও পেলুম না। দিদিমাকে অনুরোধ করলুম, বাড়িতে যেন তাঁরা চিঠি না-লেখেন যে আমি আসবার সময় স্টেশনে পড়ে গিয়ে হাঁটু কেটে ফেলেছি।
সেরে উঠে বেড়াতে বেরিয়ে একদিন দেখি ভণ্ডুলমামার বাড়িটা অনেক দূর গাঁথা হয়ে গেছে। কাঠ-থামাল পর্যন্ত গাঁথা হয়েছে, কিন্তু কড়ি এখনও বসানো হয়নি।
হঠাৎ এত খুশি হয়ে উঠলুম যে আছাড় খেয়ে হাঁটু কাটার কথা টের পেলে বাবা কী বলবেন, তখনকার মতো সে দুশ্চিন্তা মন থেকে মুছে গেল। উৎসাহে ও কৌতূহলে একদৌড়ে ভণ্ডুলমামার বাড়িতে গিয়ে হাজির। গাঁথুনি অনেক দিন বন্ধ আছে মনে হল, গত বর্ষার পরে বোধ হয় আর মিস্ত্রি আসেনি। ঘরের মেঝেতে খুব জঙ্গল গজিয়েচে, গাঁথুনির ফাঁকে ফাঁকে আমরুল শাকের গাছ, বাড়ির উঠোনে
বড়ো একটা সজনে গাছ প্রথম ফাল্গুনে ফুলের খই ফুটেচে। ঘুরে ঘুরে দেখলুম, ভণ্ডুলমামার বাড়িতে তিনটে ঘর, একটা ছোটো দালান, মাঝে একটা সিঁড়ির ঘর, আট-দশ ধাপ সিঁড়ি গাঁথা হয়ে গেছে। ওদিকের বড়ো ঘরটা বোধ হয় ভণ্ডুলমামার, মাঝের ঘরটাতে ছেলে-মেয়েরা থাকবে। ভণ্ডুলমামার বাপ আছে? কে জানে? তিনি বোধ হয় থাকবেন সিঁড়ির এপাশের ঘরটাতে। রান্নাঘর কোথায় হবে? বোধ হয় উঠোনের এক পাশে ওই সজনে গাছটার তলায়। ভণ্ডুলমামা ছেলে-মেয়ে নিয়ে যখন এসে বাস করবে, তখন এদের উঠোনে কী আর এমন জঙ্গল থাকবে? ছেলে-মেয়েরা ছুটোছুটি দৌড়োদৌড়ি করে খেলবে, হয়তো বাড়িতে সত্যনারায়ণের সিন্নি দেবে পূর্ণিমায় কী সংক্রান্তিতে। পুকুরপাড়ের এ জংলি চেহারা তখন একেবারে বদলে যাবে যে! আমার মামার বাড়ির এপাড়াতে এক ঘর লোক বাড়বে…ওপাড়া থেকে খেলা করে ফেরবার পথে সন্ধে হয়ে গেলেও আর ভাবনা থাকবে না…ওদের বাড়িতে আলো জ্বলবে, ছেলে-মেয়েরা কথা বলবে, কীসের আর তখন ভয়? দিব্যি চলে যাবে।
আরও বছর দুই কেটে গেল। থার্ড ক্লাসে পড়ি। মামারবাড়ি একাই গেলুম। একাই এখন সব জায়গায় যাই। ভণ্ডুলমামার বাড়ির ছাদ-পেটানো হয়ে গিয়েছে, সিমেন্টের মেঝে, দালানের বাইরে রোয়াক হয়েছে কবে আমি দেখিনি তো? রোয়াকের ওপর কেমন টিনের ঢালু ছাদ! কেবল একটুখানি এখনও বাকি, দরজা জানালায় এখনও কপাট বসানো হয়নি। বাঃ, ভণ্ডুলমামার বাড়ি তাহলে হয়ে গেল!
ভণ্ডুলমামা নাকি আজকাল বড়ো সুদখোর হয়ে উঠেছেন, মাঝে মাঝে গাঁয়ে আসেন, চড়া সুদে লোকজনকে টাকা ধার দেন, বাড়ি দেখাশুনো করেন, আবার চলে যান। মাসকতক পরে আবার এসে কাবুলিওয়ালার মতো চড়াও হয়ে সুদ আদায় করেন। গাঁয়ের লোক তাঁর নাম রেখেচে রত্নদত্ত।
তারপর এল একটা সুদীর্ঘ ব্যবধান। ছেলেবেলার মতো মামারবাড়িতে আর তত যাই-নে, গেলেও এক-আধ দিন থাকি। সেই এক-আধ দিনের মধ্যে পথে যেতে যেতে হয়তো দেখি, জঙ্গলের মধ্যে ভণ্ডুলমামার বাড়িটা তেমনি জনহীন হয়ে পড়ে আছে…বনজঙ্গল চারিপাশে আরও গভীরতর, কেউ কোনোদিন ওবাড়িতে পা দিয়েছে বলে মনে হয় না। একটা ছন্নছাড়া, লক্ষ্মীছাড়া চেহারা, শীতের সন্ধ্যায় বর্ষার দিনে, চৈত্র-বৈশাখের দুপুরে কত বার ওবাড়িটা দেখেছি, সেই একই মূর্তি…
এমনি করে বছরকয়েক কেটে গেল।
ক্রমে এন্ট্রান্স পাস দিয়ে কলকাতায় এসে কলেজে ঢুকলুম। সেবার সেকেন্ড ইয়ারের শেষ, এফ.এ. দেব, কী একটা দরকারে মামারবাড়ি গিয়েছি।
বোধ করি মাঘ মাসের শেষ। দুপুরে পুবের ঘরে জানালার ধারে খাটে শুয়ে আছি, বোধ হয় একখানা লজিকের বই পড়ছি, এমন সময়ে একজন কালো, শীর্ণকায় প্রৌঢ় লোক ঘরে ঢুকলেন। বড়ো মামিমা বললেন,—এই তোর ভণ্ডুলমামা, প্রণাম কর।
আমার সে ছেলেবেলাকার মনের অনেক পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল, বয়স হয়েছে, কলেজে পড়ি; নানা ধরনের লোকের সঙ্গে মিশেছি, সুরেন বাঁড়য্যে ও বিপিন পালের বক্তৃতা শুনেছি, স্বদেশি মিটিঙে ভলান্টিয়ারি করেছি, জীবনের দৃষ্টিভঙ্গিই গেছে বদলে, তখন মনের কোন গভীর তলদেশে আরও পাঁচটা পুরোনো দিনের আদর্শের ও কৌতূহলের বস্তুর ভ্রুপের সঙ্গে ভণ্ডুলমামা ও তাঁর বাড়িও চাপা পড়ে গিয়েছে। তাই ঈষৎ অবজ্ঞামিশ্রিত চোখে সামান্য একটু কৌতূহলের সঙ্গে চেয়ে দেখলুম মাত্র—ভণ্ডুলমামার বয়স পঞ্চাশের ওপর হবে, টিকিতে একটা মাদুলি বাঁধা, গলায় কীসের মালা, কাঁচাপাকা একমুখ দাড়ি। এই সেই ছেলেবেলাকার ভণ্ডুলমামা! উদাসীনভাবে প্রণামটা সেরে ফেললুম।
ভণ্ডুলমামা কিন্তু আমার সঙ্গে খুব আলাপ করলেন, একটু গায়েপড়েই যেন। আমি কোন কলেজে পড়ি, কোন মেসে থাকি, কবে আমার পরীক্ষা ইত্যাদি নানাপ্রশ্নে আমায় জ্বালাতন করে তুললেন। আজকাল তিনি কলকাতায় চাকরি করেন, বাগবাজারে বাসা, তাঁর বড়ো ছেলেও এবার ম্যাট্রিক দিয়ে ফার্স্ট ইয়ারে পড়ছে—এসব খবরও দিলেন।
আমি জিজ্ঞেস করলুম,—আপনাদের এখানকার বাড়িতে ছেলে-মেয়ে আনবেন না?
ভণ্ডুলমামা বললেন, আনব, শিগগিরই আনব বাবা। এখনও একটু বাকি আছে, একটা রান্নাঘর আর একটা কুয়ো—এ দুটো করতে পারলেই সব এনে ফেলি। কলকাতায় বাসাভাড়া আর দুধের খরচ জোগাতেই…সেইজন্যেই তো খেয়ে-না খেয়ে দেশে বাড়িটা করলুম, তবে ওই একটুখানি যা বাকি আছে…তা ছাড়া চিলেকোঠার ছাদটা এখনও এইবারেই ভাবছি শ্রাবণ মাসের দিকে ওটাও শেষ করব।
বলে কী! এখনও বাকি! জ্ঞান হয়ে পর্যন্ত দেখে আসছি, ভণ্ডুলমামার বাড়ি উঠছে! এ তাজমহল নির্মাণের শেষ বেঁচে থেকে দেখে যেতে পারব তো!
ভণ্ডুলমামা আপন মনেই বলে যেতে লাগলেন—সামান্য চাকরি, ছাপোষা মানুষ বাবা, কাচ্চাবাচ্চা খাইয়ে যা থাকে তাতেই তো বাড়ি হবে? এখন তো বাসায় বাসায় কাটচে, আজ যদি চাকরি যায় তবে ছেলেপুলে নিয়ে কোথায় দাঁড়াব, তাই ভেবে আজ চোদ্দো-পনেরো বছর ধরে একটু একটু করে বাড়িটা তুলচি। তবে এইবার আর দেরি হবে না, আসচে বছর সব এনে ফেলব। জায়গাটা বড়ো ভালোবাসি।
ভণ্ডুলমামা বললেন তো চোদ্দো-পনেরো বছর, কিন্তু আমার মনে হল ভণ্ডুলমামার বাড়ি উঠছে আজ থেকে নয়, জীবনের পিছন ফিরে চেয়ে দেখলে যতদূর দৃষ্টি চলে ততকাল ধরে…যেন অনন্তকাল, অনন্ত যুগ ধরে ভণ্ডুলমামার বাড়ির ইট একখানির পর আর একখানি উঠছে…শিশু থেকে কবে বালক হয়েছিলুম, বালক থেকে কিশোর, কৈশোর কেটে গিয়ে এখন প্রথম যৌবনের উন্মেষ, আমার মনে এই অনাদ্যন্ত মহাকাশ বেয়ে কত শত জন্মমৃত্যু, সৃষ্টি ও পরিবর্তনের ইতিহাসের মধ্য দিয়ে ভণ্ডুলমামার বাড়ি হয়েই চলেছে…ওরও বুঝি আদিও নেই, অন্তও নেই।
পরের বছর আবার ভণ্ডুলমামার সঙ্গে কলকাতাতেই দেখা। আমি তখন থার্ড ইয়ারে পড়ি। ভণ্ডুলমামা বললেন—এসো একবার আমাদের বাসায়। তোমার মামি তোমায় দেখলে খুশি হবে।—সামনের রবিবার তোমার নেমন্তন্ন রইল, অবিশ্যি অবিশ্যি যাবে।
গেলুম, ভণ্ডুলমামার ছেলেদের সঙ্গেও আলাপ হল। ভণ্ডুলমামা অনুযোগের সুরে বললেন,—ওদের বলি, যা একবার এই সময়ে। আষাঢ় মাসে দেশে গিয়ে উঠোনে খাসা বরবটি আর শিম লাগিয়ে রেখে এসেছি, মাচাও বেঁধে রেখে এসেছি,—তা কেউ কী কথা শোনে?
মামিমা ঝংকার দিয়ে বলে উঠলেন,—যাবে সেখানে কেমন করে শুনি? কোনো ঘরে বাস করবার জো নেই, ছাদ ফুটো হয়ে জল পড়ে। জলের ব্যবস্থা নেই বাড়িতে, শুধু শিম আর বরবটির পাতা চিবিয়ে তো মানুষে…তাতে বাড়ি হাট আলগা, পাঁচিল নেই।
ভণ্ডুলমামা মৃদু প্রতিবাদের সুরে ভয়ে ভয়ে যা বললেন তার মর্ম এই যে, মানুষ বাস না-করলেই বাড়িতে বট-অশ্বথের গাছ হয়, ছাদ আঁটা হয়ে গেছে আজ অনেকদিন, কিন্তু কেউ বাস তো করে না। বাড়ি কাজেই খারাপ হতে থাকে। তবুও তিনি বছরে দু-তিনবার যান বলে এখনও ঘরদোর টিকে আছে। পাতকুয়োর আর কত খরচ? চৈত্র মাসের দিকে না-হয় করে দেওয়া যাবে। আর তোমরা সবাই যদি যাও, পাঁচিল আষাঢ় মাসেই করে দেওয়া যাবে।
বুঝলুম পাঁচিল পাতকুয়ো এখনও বাকি। ভণ্ডুলমামার বাড়ি এখনও শেষ হয়নি, এখনও কিছু বাকি আছে। কিন্তু এতদিন ধরে ব্যাপারটা চলচে যে, এক দিক গড়ে উঠতে অন্য দিকে ধরেছে ভাঙন।
এর পরে মামারবাড়ি গিয়ে দু-একবার দেখেছি ভণ্ডুলমামা দু-পাঁচ দিনের ছুটি নিয়ে বাড়িতে এসে আছেন। এটা সারাচ্ছেন, ওটাতে বেড়া বাঁধছেন, এগাছটা খুঁড়ছেন, ওগাছটা কাটছেন। ছেলেরা আসতে চায় না কলকাতা ছেড়ে। নিজেকেই আসতে হয়, দেখাশোনো করতে হয় বলে একদিন সলজ্জ কৈফিয়তও দিলেন।…পাঁচিল? হ্যাঁ তা পাঁচিল—সম্প্রতি একটু টানাটানি যাচ্ছে…সামনের বর্ষায়…ঘরদোর বেঁধেছি সারাজীবন খেটে, ওই আমার বড়ো আদরের জায়গা তোরা না-থাকিস, আমিই গিয়ে থাকি।
আমি বললুম,—ওখানে কেমন করে থাকেন? সারাগাঁয়েই তো মানুষ নেই, মামারবাড়ির পাড়া তো একেবারে জনশূন্য হয়ে গেছে।
—কী করি বাবা, ওই বাড়িখানার ওপর বড়ো দম আমার যে। দেখো, চিরকাল পরের বাসায়, পরের বাড়িতে মানুষ হয়ে ঘরের কষ্ট বড়ো পেয়েছিলুম—তাই ঠিক করি বাড়ি একখানা করবই। ছেলেবেলা থেকে ওই গাঁয়েই কাটিয়েছি, ওখানটা ছাড়া আর কোথাও মন বসে না। চিরকাল ভাবতুম রিটায়ার করে ওখানেই বাস করব। একটা আস্তানা তো চাই, এখন না-হয় ছেলেপিলে নিয়ে বাসায় বাসায় ঘুরছি, কিন্তু এর পরে দাঁড়াব কোথায়? তাই জলাহার করেও সারাজীবন কিছু কিছু সঞ্চয় করে ওই বাড়িখানা করেছিলুম। তা ওরা তো কেউ এল না—আমি নিজেই থাকি। না-থাকলে বাড়িখানা তো থাকবে না—আর এককালে-না-এককালে
ছেলেদের তো এসে বসতেই হবে বাড়িতে। কলকাতার বাসায় বাসায় তো চিরকাল কাটবে না।
তারপর মামাদের মুখে ভণ্ডুলমামার কথা আরও সব জানা গেল। ভণ্ডুলমামা একা বিজন বনের মধ্যে নিজের বাড়িখানায় থাকেন। তাঁর এখনও দৃঢ় বিশ্বাস তাঁর ছেলেরা শেষপর্যন্ত ওই বাড়িতেই গিয়ে বাস করবে। তিনি এখনও এজায়গাটা ভাঙচেন, ওটা গড়চেন, নিজের হাতে দা নিয়ে জঙ্গল সাফ করচেন। ছেলেদের সঙ্গে বনে না—ওই বাড়ির দরুনই মনান্তর, স্ত্রীও ছেলেদের দিকে। ছেলেরা বাপকে সাহায্যও করে না। ভণ্ডুলমামা গাঁয়ে একখানা ছোটো মুদির দোকান করেছিলেন—লোক নেই তার কিনবে কে? যা দু-একঘর খদ্দের জুটেছিল—ধার নিয়েই দোকান উঠিয়ে দিলে। এখন ভণ্ডুলমামা এগাঁ-ওগাঁ বেড়িয়ে কোনো চাষার বাড়ি থেকে দু-কাঠা চাল, কারুর বাড়ির পাঁচটা বেগুন—এইরকম করে চেয়েচিন্তে এনে বাড়িতে হাঁড়ি চড়িয়ে দুটো ফুটিয়ে খান।
তারপর ধীরে ধীরে অনেক বছর কেটে গেল। আমি ক্রমে বি.এ. পাস করে চাকরিতে ঢুকলুম। মামারবাড়ি আর যাইনে, কারণ সে-গ্রাম আর যাবার যোগ্য নয়। মামারবাড়ির পাড়ার গাঙ্গুলীরা, রায়েরা, ভড়েরা সব একে একে মরে-হেজে গেল, যারা অবশিষ্ট রইল তারা বিদেশে চাকরি করে, ম্যালেরিয়ার ভয়ে গ্রামের ত্রিসীমানা মাড়ায় না। ওপাড়াতেও তাই জীবন মজুমদারের প্রকাণ্ড দোতলা বাড়ির ছাদ ভেঙে ভূমিসাৎ হয়ে গিয়েছে, শুধু একদিকের দোতলাসমান দেয়ালটা দাঁড়িয়ে আছে। যে পুজোর দালানে ছেলেবেলায় কত উৎসব দেখেছি, এখন সেখানে বড়ো বড়ো জগডুমুরের গাছ, দিনেই বোধ হয় বাঘ লুকিয়ে থাকে। বিখ্যাত রায়দিঘি মজে গিয়েছে, দামে বোঝাই, জল দেখা যায় না, গোরু-বাছুর কচুরিপানার দামের ওপর দিয়ে হেঁটে দিব্যি পার হতে পারে।
সন্ধ্যারাতেই গ্রাম নিশুতি হয়ে যায়। দু-এক ঘর নিরুপায় গৃহস্থ যারা নিতান্ত অর্থাভাবে এখনও পৈতৃক ভিটেতে ম্যালেরিয়া-জীর্ণ হাতে সন্ধ্যাদীপ জ্বালাচ্ছে, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হতে-না-হতেই তারা প্রদীপ নিবিয়ে শয্যা আশ্রয় করে—তারপর সারারাত ধরে চারিধারে শুধু প্রহরে প্রহরে শৃগালের রব ও নৈশপাখির ডানা ঝটাপটি!
আমার মামারাও গ্রামের ঘর-বাড়ি ছেড়ে শহরে বাসা করেছেন। ছোটোমামার ছেলের অন্নপ্রাশন উপলক্ষ্যে সেখানে একবার গিয়েছি। ব্রাহ্মণভোজনের কিছু আগে একজন শীর্ণকায় বৃদ্ধ একটা পুঁটলি হাতে বাড়িতে ঢুকলেন। এক-পা ধুলো, বগলে একটা ময়লা সাদা কাপড় বসানো বাঁশের বাঁটের ছাতা। প্রথমটা চিনতে পারিনি, পরে বুঝলুম। ভণ্ডুলমামা এত বুড়ো হয়ে পড়েছেন এর মধ্যে!…শহরে এসে মামাদের নতুন সভ্য, শৌখিন আলাপি বন্ধুবান্ধব জুটেছে, তাদের পোশাক পরিচ্ছদের ধরনে ও কথাবার্তার সুরে ভণ্ডুলমামা কেমন ভয় খেয়ে সংকোচের সঙ্গে নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকদের শতরঞ্চির এককোণে বসলেন। তিনিও নিমন্ত্রিত হয়েই এসেছিলেন বটে, কিন্তু মামারা তখন শহুরে বন্ধুদের আদর-অভ্যর্থনায় মহা ব্যস্ত। তাঁর আগমন কেউ বিশেষ লক্ষ করেছে এমন মনে হল না।
আমি গিয়ে ভণ্ডুলমামার কাছে বসলুম। চারিধারে অচেনা মুখের মধ্যে আমায় দেখে ভণ্ডুলমামা খুব খুশি হলেন। আমি জিজ্ঞেস করলুম—আপনি কী কলকাতা থেকে আসছেন?
ভণ্ডুলমামা বললেন—না বাবা, আমি রিটায়ার করেছি আজ বছরপাঁচেক হবে। গাঁয়ের বাড়িতেই আছি। ছেলেরা কেউ আসতে চায় না।
অন্নপ্রাশন শেষ হয়ে গেল। ভণ্ডুলমামা কিন্তু মামারবাড়ি থেকে আর নড়তে চান। চার-পাঁচ দিন পরে কিছু চাল-ডাল ও বাসি সন্দেশ-রসগোল্লা নিয়ে দেশে রওনা হলেন। পায়ে দেখি কটক থেকে কিনে আনা বড়োমামার সেই পুরোনো চটিজুতোজোড়া। আমায় দেখিয়ে বললেন—নবীন কটক থেকে এনেছে, দেখে বড়ো শখ হল, বয়স হয়েছে কবে মরে যাব, বললুম তা দাও নবীন, জুতোজোড়াটা পুরোনো হলেও এখনও দু-তিন মাস যাবে। বাড়িতে একজোড়া রয়েছে, আঙুলে বড়ো লাগে বলে খালি পায়েই–
তিনি বাড়ির বার হয়ে গেলেন। আমি চেয়ে চেয়ে দেখলুম শীর্ণকায় ভণ্ডুলমামা ভারী চালডালের মোটের ভারে একটু সামনের দিকে ঝুঁকে চটিজুতোয় ফটাং ফটাং শব্দ করতে করতে স্টেশনের পথে চলেছেন। হঠাৎ আমার মনে তাঁর উপরে আমার বাল্যের সেই রহস্যময় স্নেহ ও অনুকম্পার অনুভূতিটুকু কতকাল পরে আবার যেন ফিরে এল। আমি চেঁচিয়ে বললুম—একটু দাঁড়ান মামা, আপনাকে তুলে দিয়ে আসি। ভণ্ডুলমামার পুটুলিটা নিজের হাতে নিলুম, টিকিট করে তাঁকে গাড়িতে তুলেও দিলুম। ট্রেনে ওঠবার সময় একমুখ হেসে বললেন—যেও না হে একদিন, বাড়িটা দেখে এসো আমার—খাসা করেছি—কেবল পাঁচিলটা এখনও যা বাকি। কী করি, আমার হাতে আজকাল আর তো কিছু নেই, ছেলেরা নিজেদের বাসার খরচই চালিয়ে উঠতে পারে না—অবিশ্যি ওদের জন্যেই তো সব। দেখি, চেষ্টায় আছি—সামনের বছরে যদি…
ভণ্ডুলমামার সঙ্গে আর আমার দেখা হয়নি। কিন্তু এর মাসকতক পরে তাঁর বড়োছেলে হরিসাধনের সঙ্গে কলকাতায় দেখা হয়েছিল। ম্যাকমিলান কোম্পানির বাড়িতে চাকরি করে, জিনের কোট গায়ে, হাতে বইয়ের আকারে খাবারের কৌটো, মুখে একগাল পান—বউবাজারের ফুটপাত দিয়ে বেলা দশটার সময় অফিসে যাচ্ছে। আমিই ভণ্ডুলমামার কথা তুললুম। হরিসাধন বললে—বাবা দেশের বাড়িতেই আছেন—আমরা বলি আমাদের সংসারে এসে থাকুন, তাতে রাজি নন। বুদ্ধিসুদ্ধি তো কিছু ছিল না বাবার, নেইও—সারাজীবন যা রোজগার করেছেন ওই জঙ্গলের মধ্যে এক বাড়ি করতে গিয়ে সব নষ্ট করেছেন, নইলে আজ হাজার চার-পাঁচ টাকা হাতে জমত। ওগাঁয়ে যাবেই বা কে? রামো:, যেমন জঙ্গল তেমনি ম্যালেরিয়া—তা ছাড়া লোকজন নেই, অসুখ হলে একটা ডাক্তার নেই—চার-পাঁচ হাজার টাকা খরচ হয়ে গেছে বাড়ির পিছনে, বেচতে গেলে এখন ইট-কাঠের দরেও বিক্রি হবে ভেবেছেন? কে নিতে যাবে, পাগল আপনি?
আমি বললুম—কথাটা ঠিক বটে। কিন্তু ভেবে দেখো, তোমার বাবা যখন বাড়িটা প্রথম আরম্ভ করেছিলেন, তখন জাজ্বল্যমান গ্রাম। বাড়িটা তৈরি করতে এত দেরি হয়ে গেল যে ইতিমধ্যে গাঁ হয়ে গেল শ্মশান, লোকজন উঠে অন্যত্র চলে গেল, আর সেই সময় তোমাদের বাড়ির গাঁথুনিও শেষ হল। কার দোষ দেবে?
তারপর ভণ্ডুলমামার আর কোনো সংবাদ রাখিনি অনেককাল। বছরতিনেক আগে একবার মেজোমামা চেঞ্জে গিয়েছিলেন দেওঘরে। পুজোর ছুটিতে আমিও সেখানে যাই। তাঁর মুখেই শুনলুম ভণ্ডুলমামা সেই শ্রাবণেই মারা গিয়েছেন। অসুখবিসুখ হয়ে ক-দিন ঘরের মধ্যেই ছিলেন, কেউ বিশেষ দেখাশোনা করেনি, আর আছেই বা কে গাঁয়ে যে দেখবে? এ অবস্থায় ঘরের মধ্যে মরে পড়েছিলেন, দু-তিন দিন পরে সবাই টের পায়, তখন ছেলেদের টেলিগ্রাম করা হয়। ভণ্ডুলমামার এইখানেই শেষ।
এর পর আমি আর কখনো মামারবাড়ির গ্রামে যাইনি, হয়তো আর কোনোদিন যাবও না, বাড়িটাও আর দেখিনি, কিন্তু জ্ঞান হয়ে পর্যন্ত যে বাড়িটা গাঁথা হতে দেখেছি, সেটা আমার মনের মধ্যে একটা অদ্ভুত স্থান অধিকার করে আছে। আমার কল্পনায় দেশের মামারবাড়ির গ্রামের, একগলা বনের মধ্যে শীতের দিনের সন্ধ্যায় ভণ্ডুলমামার বাড়িটা একটা কায়াহীন উদ্দেশ্যহীন রূপ নিয়ে মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে থাকে সেই গাছ-গজানো উঠোনটাতে, ঢোকবার পথ বনে ঢাকা, দরজা জানলার কপাট নেই, থামে থামে কাঠােমাল পর্যন্ত গাঁথা হয়েছে।
আমার জীবনের সঙ্গে ভণ্ডুলমামার বাড়িটার এমন যোগ কী করে ঘটল সেটা আজ ভেবে আশ্চর্য হয়ে যাই—আমার গল্পের আসল কথাই তাই। অমন একটা সাধারণ জিনিস কেন আমার এমন মন জুড়ে বসে রইল, অথচ কত বড়ো বড়ো ঘটনা তো বেমালুম মন থেকে মুছেই গিয়েছে!
বিশেষ করে এইসব শীতের সন্ধ্যাতেই মনে পড়ে এইজন্য যে পাঁচ বছর বয়সে এই শীতের সন্ধ্যাবেলাতেই বাড়িটা প্রথম দেখি।
অবিনাশবাবুর ছাত্রটি মুড়ি নিয়ে এল।