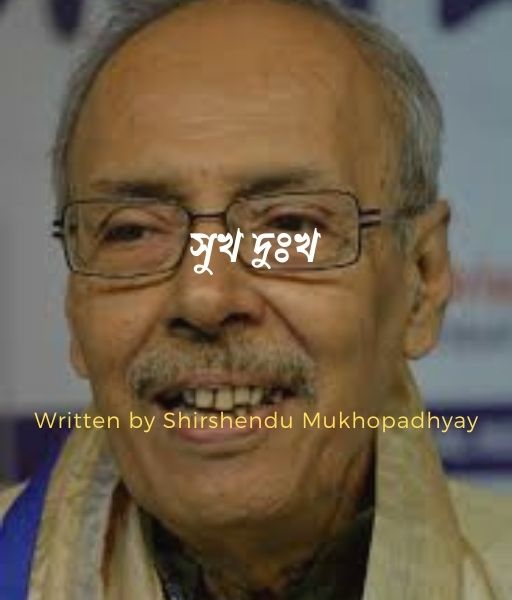প্রভাসরঞ্জন
পাঁচুদাকে দেখেই বুঝি যে লোকটার হয়ে গেছে। ব্যাচেলার মানুষ আত্মীয়স্বজন বলতেও কাছের জন কেউ নেই, মরলে কেউ বুক চাপড়াবে না, অনাথা বা অনাথ হবে না কেউ। সেই একটা সান্ত্বনা। তবু একটা মানুষ ছিল, আর থাকবে না এটা আমার সহ্য হচ্ছিল না। বলতে কি পাঁচুদার জন্য বেশ দুঃখিত হয়ে পড়েছিলাম।
ব্যাচেলারদের বেশি বয়েসে কিছু-না-কিছু বাতিক হয়ই। সম্ভবত কামের অচরিতার্থতা, নিঃসঙ্গতা ইত্যাদি মিলেমিশে তাদের বায়ুগ্রস্ত করে তোলে। পাঁচুদারও তা-ই হয়েছিল। চিরকাল তাঁর দূর সম্পর্কের যত আত্মীয়স্বজন তাঁর কাছ থেকে পয়সাকড়ি বা জিনিসপত্র হাতিয়েছে। ভণ্ড সাধু সন্ন্যাসী জ্যোতিষেরাও কাজ গুছিয়েছে কম নয়। পাঁচুদা কয়েকবারই জোচ্চোরদের পাল্লায় পড়ে ব্যবসাতে নেমে ঠকে এসেছেন। তাঁর বাপের কিছু টাকাও তিনি পেয়েছিলেন, চাকরির বেতন তো ছিলই, সব মিলেই বেশ শাঁসালো খদ্দের। লোকে ঠকাবে না কেন? প্রতি বছর মাসখানেক ধরে তীর্থ ভ্রমণ করতেন। ভারতবর্ষের এমন জায়গা নেই যেখানে যাননি। শেষ বয়সটায় বেশ কষ্ট পেলেন।
আমার মধ্যে একটা পাপবোধ ছিল। আমাদের ছেলেবেলায় যখন প্রচণ্ড অভাবের সময় চলছিল তখন এই পাঁচুদা বেশ কয়েকবার আমাদের অনাহার থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন। সেই থেকেই তাঁর প্রতি আমাদের একটা মতলববাজ মনোভাব জন্মায়। পাঁচুদা মানেই হচ্ছে আদায়ের জায়গা। তাই পাঁচুদা আমাদের বাড়িতে এলেই আমরা খুশি হতাম, যখন-তখন তাঁর বাসা বা অফিসে গিয়ে নানা কাঁদুনি গেয়ে পয়সা আদায় করেছি। আমার স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার ফি তিনিই দেন। আর, আমি তাঁর একটা সোনার বোতাম চুরি করেছিলাম।
এসব কথা তাঁকে আর বলার মানে হয় না। তবু যখন শ্যামবাজারে আয়ুর্বেদীয় হাসপাতালে তাঁকে দেখতে গিয়ে এক কঙ্কালসার চেহারাকে দেখি তখনই সেইসব পাপের কথা মনের মধ্যে জেগে ওঠে। নিজেকেই বলি–প্রভাসরঞ্জন, পাপের কথা স্বীকার করে নাও, খ্রিস্টানরা যেমন যাজকদের কাছে করে।
আমার কথা শুনে পাঁচুদা হেসে বললেন-যা যা জ্যাঠা ছেলে, চুরি করেছিস বেশ করেছিস। সেই চুরির বোম আজ তোকে দান করে দিলাম, যা।
ক্যানসারের কষ্ট তো কম নয়। শরীর শুষে ছিবড়ে করে ফেলেছে প্রতিনিয়ত। কিছু খেতে পারেন না। যা খান তা উঠে আসে ভেতর থেকে। ক্রমশ শরীর ছেড়ে যাচ্ছে তাঁর সব শক্তি। এখন কঙ্কালসার হাতখানা তুলতেও তাঁর বড় কষ্ট। মাঝে মাঝে দেখি বুকের কম্বলটা টেনে মুখ ঢাকা দিয়ে কাঁদেন। সে কান্নাও অতি ক্ষীণ। যেমন পাঁজরের খাঁচা থেকে এক বন্দি ভোমরার গুঞ্জনধ্বনি উঠে আসে।
পত্রিকা অফিস থেকে আজকাল প্রায়ই নানা জায়গায় পাঠায়। আর দু-এক মাসের মধ্যেই আমাকে পাকা চাকরিতে নেওয়া হবে। সাংবাদিকের এই চাকরি আমার খুব খারাপ লাগছে না। কিন্তু সব সময়ে একটা এই দুঃখ, আমি নানা দেশ ঘুরে যে প্রযুক্তি শিখেছি তা কোনও কাজে লাগল না। জীবনের দশ দশটা বছর আমি বৃথা অন্বেষণে কাটিয়ে এসেছি। আয়ুক্ষয়।
সুইজারল্যান্ডে আমাদের কারখানা দেখতে সেবার এক জাপানি প্রতিনিধি দল এল। বেটে বেঁটে চেহারার হাসমুখ, বুদ্ধির আলোলা ছোট ছোট চোখের মানুষ। প্রত্যেকেই বড় বড় ইঞ্জিনিয়ার তাদের দেশে। কারখানা দেখার অনুমতি চাইল। ওপরওয়ালা আমাকে এবং আরও কয়েকজনকে ডেকে ওদের কারখানা দেখাতে বলে দিলেন। অনুমতি পেয়ে জাপানিদের চেহারা ধাঁ করে পালটে গেল। পরনের স্যট খুলে ওভারঅল পরে নিল সবাই, খাতা-পেনসিল-পেন কম্পাস সাজিয়ে নিল। তারপর প্রতিটি যন্ত্র আর যন্ত্রাংশের মধ্যে ওরা কালিঝুলি মেখে ঢুকে যেতে লাগল। ভাল করে লাঞ্চ পর্যন্ত করল না। ভূতের মতো শুয়ে বসে দাঁড়িয়ে যন্ত্রের সমস্ত রহস্য জেনে নিতে লাগল। পরপর সাত দিন একনাগাড়ে তার কারখানাটিকে জরিপ করতে লাগল। শেষ দিকে ওদের চলাফেরা, যন্ত্রের ব্যবহার এবং কথাবার্তা শুনে হঠাৎ বুঝতে পারলাম, আমি এ কারখানায় এতকাল থেকেও যে সব রহস্য জানি না ওরা অল্প দিনেই তা সব জেনে গেছে।
জাপানিরা দেশে ফিরে যাওয়ার দু বছরের মধ্যে জাপান থেকেই বিশ্বের বাজারে কম্প্রেসর মেশিন ছাড়া হল। সুইস কম্প্রেসরের চেয়ে তা কোনও অংশে খারাপ তো নয়ই, বরংগামে অনেক সস্তা। এমনকী ওরা সুইস যন্ত্রের নকল করেছে বলেও মনে করার কারণ নেই। যন্ত্রের মৌল রহস্যটা জেনে গিয়ে ওরা ওদের মতো যন্ত্র বানিয়েছে।
এ ঘটনার বছরখানেকের মধ্যেই একটি ভারতীয় প্রযুক্তিবিদ্যার দল সুইজারল্যান্ড যায়। ব্যল-এ এসে তারা আমাদের কারখানাতেও হানা দিয়েছিল। স্মিড সাহেব আমাকে ডেকে বললেন–তোমার দেশের লোকদের তুমিই এসকর্ট করে নিয়ে কারখানা দেখাও।
ভারতের লোক এসেছে শুনে আমি খুবই উৎসাহ বোধ করি। দলে একজন বাঙালিও ছিলেন, আমি তাঁর সঙ্গে বাংলায় কথা বলতে তিনি একটু অবাক হলেন। কিন্তু তিনি দেশে খুব বড় চাকরি করেন, আর আমি এ কারখানার একজন স্কিলড লেবার মাত্র। তাই তিনি আমার সঙ্গে বিশেষ মাখামাখি করলেন না, একটু আলগা আলগা ভালবাসা দেখালেন। মোট ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে তাঁরা অত বড় কারখানাটার হাজারো যন্ত্রপাতি দেখে ফেললেন। যা-ই দেখাই তা-ই দেখেই বলেন–ওঃ, ভেরি গুড। হাউ নাইস! ইস ইট! যন্ত্রপাতি তাঁরা ছুঁয়েও দেখলেন না। তারপর ম্যানেজারের ঘরে বসে কফি খেয়ে চলে গেলেন। পরে স্মিড সাহেব আমাকে ডেকে বললেন-তোমার দেশের লোকেরা এত অল্প সময়ে এত বড় প্রোজেক্টের সব বুঝে ফেলল?
তখন আমি ঠিক করেছিলাম এরা যা করেনি তা আমাকেই করতে হবে। তারপর কিছুদিন আমি একা একা পুরো যন্ত্রপাতির নকশা কপি করতে শুরু করি। এমনিতেই ভূতের মতো খাটুনি ছিল, তার ওপর বাড়তি খাটুনি যোগ হল। হয়তো পেরেও যেতাম। কিন্তু ঠিক সেই সময় বিয়ে ভেঙে যাওয়ায় আমার ভিতরকার সব উৎসাহ নিভে যায়। তবু যা শিখেছিলাম, যা কপি করেছিলাম তাও বড় কম নয়। যে-কোনও ইঞ্জিনিয়ারের চেয়ে আমার প্রযুক্তির ধারণা অনেক প্রাঞ্জল এবং বাস্তব। আমি হাতেকলমে যন্ত্র চালিয়েছি। যন্ত্রের সব চরিত্রই আমার জানা। এখনও ভারী কম্প্রেসর মেশিনের যে-কোনও কারখানায় আমার অভিজ্ঞতা অসম্ভব রকমের কার্যকর হতে পারে।
কিন্তু তা হল না। আমি এখন নানা চটুল বা রাশভারী বিষয় নিয়ে খবরের কাগজে ফিচার লিখছি। লিখতে আমার খারাপ লাগে না ঠিকই, কিন্তু সব সময়েই আমার অধীত বিদ্যার অপচয়ের জন্য কষ্ট হয়, যা কষ্ট করে শিখে এসেছি তা এ দেশে কাজে লাগল না। অবশ্য আমি এখানকার কলকারখানায় চাকরি করতে আর উৎসাহীও নই। আমি চেয়েছিলাম নিজেই একটি কারখানা প্রতিষ্ঠা করব।
এখন টাইপ রাইটারের খটখটানির মধ্যে একরকমের নতুন জীবনের খবর পেয়ে যাচ্ছি। মধু মল্লিক এসে প্রায়ই খবর দেন, আমার ফিচারগুলো কাজের হচ্ছে।
মধু মল্লিক একদিন এসে বললেন-কস্ট অফ প্রোডাকশন কমিয়ে আনার ব্যাপারে আপনার ফিচারটা সাঘাতিক হয়েছে। কিন্তু প্রভাসভাবু, আমাদের সবচেয়ে বেশি কটেজ আর স্মল স্কেল। শুধু হেভি ইন্ডাস্ট্রি দিয়ে এদেশের ইনকাম স্টেবল করা যাবে না। আপনি কি এ কথা মানেন?
আমি মানি। মধু মল্লিকও মানেন দেখে খুব খুশি হলাম। বললাম-কটেজ বা স্মল স্কেল না থাকলে দেশের প্রাণ নষ্ট হয়ে যায় এ আমি স্বীকার করি। তা ছাড়া এদেশের লক্ষ লক্ষ লোক ওইসব নিয়ে আছে। কৃষিভিত্তিক সমাজকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে ওটার খুবই দরকার।
–লিখুন না একবার স্মল আর কটেজ নিয়ে। মধু মল্লিক বললেন। কাজ সহজ নয় তবে আমার অফিস থেকে প্রচুর সাহায্য করা হল এ ব্যাপারে! কুটির এবং ছোট ছোট শিল্পের ওপর পত্রিকা চারটে সিরিয়াল পাবে। আমাকে সে জন্য গোটা পশ্চিমবাংলার গাঁয়ে গঞ্জে চলে যেতে হল। সরকারি লোকদের সঙ্গে দেখা করা। সেই সূত্রেই জয়দেবের সঙ্গে দেখা বাঁকুড়ায়। ভারী দুঃখী চেহারার লোক এবং খুবই ভালমানুষ! ডক্টরেট হয়েছেন সম্প্রতি, জানেনও বিস্তর। একখানা নতুন বই লিখেছেন ফোক আর্ট সম্পর্কে। কথায় কথায় বিয়ের কথা উঠতে আমি বলেছিলাম আমার বউ-ছেলে সব পর হয়ে গেছে। সেই ভ্যাকুয়ামটা পূর্ণ করতে এখন আমার অনেক কাজ চাই। নইলে একা হলেই ভূতে পায়।
জয়দেব আমার হাত চেপে ধরে বললেন–আমার কেসও আপনার মতো। আমার ছেলেপুলে নেই, কিন্তু বউ ছিল। প্রায় বিনা কারণে সে আমাকে ছেড়ে গেছে।
যোগাযোগটা খুবই অদ্ভুত। অলকার স্বামীকে যে এত সহজে দুম করে খুঁজে পাব কখনও ভাবিনি। পরিচয় বেরিয়ে পড়তে যখন অলকার খবর দিলাম তখন জয়দেব হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে জিজ্ঞেস করল–ও কি আবার বিয়ে করবে?
না, না।
—ওকে বলবেন, মেয়েদের দুবার বিয়ে হতে নেই। সেটা খুব খারাপ। ও আমাকে ছেড়ে যাওয়ায় আমাদের পরিবারে মস্ত ঝড়ের ধাক্কা গেছে। এখনকার ছেলেমেয়েরা তো কখনও সমাজ বা পরিবারের পারসপেকটিভে দাম্পত্য জীবনের কথা ভাবেনা। যদি ভাবত তা হলে অলকা অত সহজে ছেড়ে যেতে পারত না। অপছন্দের স্বামীকেও মানিয়ে নিত। আর এও তো সত্যি যে, আজকের অপছন্দের লোক কালই প্রিয়জন হয়ে উঠতে পারে, যেমন আজকের প্রিয়জন হয়ে যায় কাল দুচোখের বিষ!
সত্যি কথা। সহ্য করা বা বহন করা আজকের মানুষের ধাতে নেই। অপছন্দের জিনিস তারা খুব তাড়াতাড়ি বাতিল করে দেয়। নতুন জিনিস নিয়ে আসে। আর এইভাবেই তাদের স্বভাব হয়ে উঠেছে পিছল ও বিপজ্জনক।
আমি বললাম-আপনি কি এখনও অলকাকে ভালবাসেন?
কেন একরকম লোভী শিশুর মতো তাকাল জয়দেব। অনেকক্ষণ বাদে মাথা নেড়ে বলল–তাতে কী যায় আসে! ও তো আর আমাকে ভালবাসে না!
আমি চিন্তা করে বললাম–দেখুন, ভালবাসাটা সব সময়েই তো আর হুস করে মাটি খুঁড়ে ফোয়ারার মতো বেরোয় না। ওটা একটা প্র্যাকটিসের ব্যাপার। ভালবাসার চেষ্টা থেকেই ভালবাসা আসে।
–সে হতে পারে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সেই চেষ্টারও অভাব রয়েছে। তিলমাত্র মমতা থাকলে তাকে বাড়িয়ে বিরাট ভালবাসা জন্মাতে পারে। কিন্তু যেখানে সেই তিলমাত্রও নেই?
আমি ভাবিত হয়ে পড়ি। এবং ফিরে আসি।
কলকাতায় এসেই একটু ঝামেলায় পড়ে গেলাম।
একদিন অনেক রাত অবধি টাইপ মেশিন চালিয়ে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়েছি। ভোররাতে এসে ঘুম ভাঙাল সুহাস।
দরজা খুলে তাকে দেখে খুব খুশি হই না, বললাম–কী রে, কী চাস?
মার খুব অসুখ। এখন-তখন অবস্থা। কী করব।
শরীরে একটা ধনুকের টংকার বেজে উঠল। মা!
কথা আসছিল না মুখে। অবশ হয়ে চেয়েছিলাম, সুহাস বলল–কিছু টাকা দাও।
টাকা দেব? অবাক হয়ে বলি–টাকা দেব সেটা বড় কথা কী। আগে গিয়ে মাকে একটু দেখি! তুই ট্যাক্সি ডাক তো।
বলে আমি ঘরে গিয়ে জামাকাপড় পরছিলাম। সুহাস ট্যাক্সি আনতে যায়নি, দরজার কাছে দোনোমনো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চোখে পড়তে বলল–তুমি বিশ্রাম নাও না! এক্ষুনি যাওয়ার দরকার নেই খুব একটা। অবস্থা যতটা খারাপ হয়েছিল ততটা এখন নয়। তুমি ব্যস্ত মানুষ, দু-চারদিন পরে যেয়ো।
ওর কথা বুঝতে পারছিলাম না একদম। আবোল-তাবোল বকছে? এই বলল খারাপ অবস্থা, আবার বলছে তত খারাপ নয়। কেমন একটু সন্দেহ হল মনে। বললাম-তোর মুখে সত্যি কথাটথা আসে তো ঠিক?
বাঃ, মিথ্যে বলছি নাকি?
আর অসুখ, তা আমাকে যেতে বারণ করছিস কেন?
–তোমার অসুবিধের কথা ভেবেই বলেছি। যাবে তো চলো।
ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে আয়, আমি যাব।
দমদমের বাসার কাছে এসে যখন ট্যাক্সির ভাড়া মেটাচ্ছি তখন সুহাস এই একটু আসছি বলে কথায় কেটে পড়ল। বাড়িতে ঢুকে দেখি মা পিছনের বারান্দায় বসে কুলোয় রেশনের চাল বাছছে।
আমি গিয়ে মার কাছে বসতেই মা কুলো ফেলে আমাকে দুহাতে আঁকড়ে ধরে বলল, ওরা বলে তুই নাকি খুব খারাপ হয়ে গেছিস! কোনও এক বিধবা না সধবার সঙ্গে নাকি তোর বিয়ে সব ঠিক?
আমি স্তম্ভিত হয়ে মাকে দেখি। অনেকক্ষণ বাদে বলি-তোমার কী হয়েছে? শুনলাম তোমার খুব অসুখ।
হলে বাঁচি বাবা। সে অসুখ যেন আর ভাল না হয়। কিন্তু গতরে তো অসুখও একটা করে না তেমন।
সুহাস আজ সকালে গিয়ে তোমার অসুখের নাম করে টাকা চেয়েছিল।
মা হাঁ করে একটু চেয়ে থেকে বলে–ওর অবস্থা খুব খারাপ বাবা, নুন আনতে পান্তা ফুরায়। তাই বোধহয় এই ফিকির করেছিল।
রান্নাঘর থেকে নিমি খুব হাসিমুখে এককাপ চা নিয়ে বেরিয়ে এসে বলল-দাদাকে কতদিন বাদে দেখলাম। খুব ব্যস্ত শুনি।
আমি গম্ভীর হয়ে বলি-সুহাস কোথায় গেল বউমা?
এসে পড়বে এক্ষুনি। বসুন না।
আমি মাথা নেড়ে বললাম-ও আসবে না, আমি জানি। বউমা, তুমি মার কাপড়চোপড় যা আছে গুবিয়ে দাও। আমি মাকে নিয়ে যাব।
মা শুনে কেমন ধারা হয়ে গিয়ে বলল–সে কী কথা বলিস। এখন আমি কোথায় যাব?
আমি চড়া গলায় বললাম–যেতেই হবে। এখানে তোমার গুণের ছেলে তোমাকে ভাঙিয়ে ব্যবসা শুরু করতে চলেছে যে! কত বড় সাহস দেখেছ।
অমনি নিমি ঘর থেকে তেড়ে এসে বলল–বেশি বড় বড় কথা বলবেন না বলে দিচ্ছি। আপনার কীর্তিরও অনেক জানি!
দুচার কথায় প্রচণ্ড ঝগড়া লেগে গেল। পাড়ার লোক এসে জুটতে লাগল চারদিকে।
আমি মাকে বললাম–মা, তোমাকে যেতেই হবে। এ নরকে আর নয়।
বোধহয় আমাকে ঝঞ্ঝাট থেকে বাঁচাতেই মা উঠে গিয়ে একটা টিনের তোরঙ্গ গুছিয়ে নিল। আমি মাকে নিয়ে চলে এলাম।
কয়েকদিন মন্দ গেল না। মা রান্না বান্না করে, আমি কাজে যাই। মধু মল্লিকের সবাই মার দেখাশুনা করে। এমনকী অলকা পর্যন্ত খোঁজ খবর নিয়ে যায়। কিন্তু এতসব ভদ্রলোক এবং লেখাপড়া জানা পরিবেশে থেকে মার অভ্যাস নেই। সব সময় তটস্থ ভাব। মাকে নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় অবশ্য আমার ছিল না, দিনরাত ঘুরি, রাত জেগে ফিচার টাইপ করি।
দিন পনেরো পরে মা একদিন মিনমিন করে বলল–প্রভাস, একবার বরং দমদম থেকে ঘুরে আসি।
গম্ভীর হয়ে বলি কেন?
মা ভয় খেয়ে বলে সুহাস আর নিমি যেমনই হোক ওদের ছেলেমেয়েগুলো আমাকে ছাড়া থাকতে পারে না।
আমি বললাম-মা, সুহাস আর নিমি তোমার ওপর কেমন নির্যাতন করে বলল তো! মারে নাকি?
মা শ্বাস ফেলে বলে-অমানুষের সব দোষ থাকে বাবা। মাকে মারবে সে আর বেশি কথা কী?
— তবু যেতে চাও?
ওদের কাছে যেতে চাইছি নাকি! ওই যে ছেলেমেয়েগুলো, ওরা যে মাটিতে গড়াগড়ি খেয়ে আমার জন্য কাঁদে।
কাঁদবে না, অভ্যাস হয়ে যাবে।
মা অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল তুই একটা বিয়ে কর। তখন এসে পাকাপাকিভাবে তোর কাছে থাকব।
আমি বললাম বাবার কাছে যাবে মা? চাও তো বন্দোবস্ত করে দিই।
যাব বইকী! যাবন। শীতটা আসুক।
বুঝলাম, এ জন্মের মতো সুহাসের হাত থেকে মার মুক্তি নেই। সুহাস যেমনই হোক, তার করে মার রক্তের ষোত নিজের দিকে টেনে নিয়েছে! আর ফেরানো যাবে না।
মাকে একদিন ফের গিয়ে দমদমের বাড়িতে রেখে এলাম। এই ঝামেলায় আর জয়দেবের কথা তেমন মনে ছিল না। কাজের চাপও ক্রমশ বাড়ছে। হঠাৎ একদিন সাত সকালে জয়দেব নিজেই এসে হাজির।