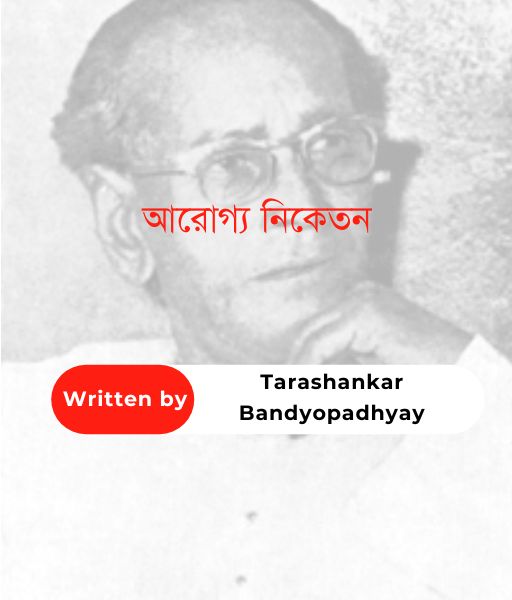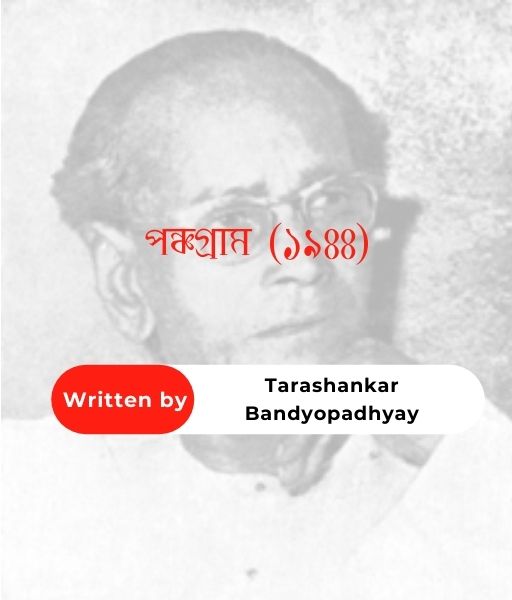দ্বিতীয় খণ্ড – চতুর্থ পর্ব : ৪.১৪
“তা কিন্তু হয় নি। সংসারে মানুষের আশার শেষ নেই, সে আকাশে ফুলফোটা দেখতে চায়, ফোটাতে চায়। কিন্তু ফুল আকাশে ফোটে না। বীরেশ্বর রায় সেদিন প্রত্যাশা করেছিলেন, হয়তো সকালে উঠে দেখবেন—”
সুরেশ্বর বললে—শুধু বীরেশ্বর রায় কেন, তোমাকে কি বলব সুলতা, সেদিন উনিশশো ছত্রিশ সালের মে মাসের রাত্রিতে সেই ডায়রী পড়ে, আমারও তার ছোঁয়াচ লেগেছিল। বীরেশ্বর রায় ঊনবিংশ শতাব্দীর আধা রোমান্টিসিজম, তাই বা কেন, বারো আনা রোমান্টি- সিজম আর চার আনা রিয়ালিজম মেশানো কালের মানুষ। ১৮৫৬ সালের অনেক পরে রামকৃষ্ণদেব সিদ্ধিলাভ করেছেন। দত্তবাড়ীর নরেন দত্ত তখনকার দিনের চার আনা রিয়া- লিজমকে ষোল আনা করে রামকৃষ্ণকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন, ঈশ্বর দেখাতে পার? সে চ্যালেঞ্জে চার আনা রিয়ালিজমও রোমান্টিসিজমের মধ্যে অতলে তলিয়ে গিয়েছিল। রামকৃষ্ণদেব নাকি তাঁকে কালীদর্শন করিয়েছিলেন। নরেন দত্ত বিবেকানন্দ হয়ে শুধু ভারতবর্ষ নয়, আমেরিকায় গিয়েও তার ঘোর ধরিয়েছিলেন। বীরেশ্বর রায় ডায়রীতে যে প্রত্যাশার কথা লিখেছেন, তা কিছুমাত্র আনরিয়াল বা অবাস্তব ছিল না। কিন্তু আমি? আমি বিংশ শতাব্দীতে সেই গ্রীষ্মের রাত্রে দরজা বন্ধ করে, পাখা বন্ধ করে ডায়রীর পাতা ওল্টাচ্ছিলাম, ঠিক ওই প্রত্যাশা করে।
অবশ্য তার কারণ ছিল। কারণ আমি জানতাম যে, ভবানী দেবী ফিরেছিলেন। তাঁর একটি কন্যা হয়েছিল। সে কন্যার বংশ বিদ্যমান। রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায়কে বীরেশ্বর রায় পোষ্যপুত্র নিয়ে বিষয় দিয়েছিলেন। তার জন্য তাঁর কন্যার তরফ থেকে পোষ্যপুত্র নাকচের মামলা দায়ের পর্যন্ত হয়েছিল। কিন্তু মামলাটা চলেনি, মিটমাট হয়ে গিয়েছিল। কি কারণে কিভাবে মিটমাট হয়েছিল, যথাসময়ে বলব। সে নিয়েও একটা ছবি আমি এঁকেছি। এবং এই মামলার মিটমাটের সময় তোমার পূর্বপুরুষ রায়বংশের এমন একটা কথা জেনেছিল, যে কথাটা প্রকাশ করবার ভয় দেখানোতেই সে খুন হয়েছিল পিদ্রু গোয়ানের হাতে। তার ছবি ওই কোণে আছে।
এখন দেখ, ওই দিনমানে, সোফিয়া বাঈজীর বাড়ীতে ওই তান্ত্রিক পাগল অপরিসীম মমতায় ওই রুগ্ন সোফি বাঈজীর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। সে চোখ মেলেছে। শুকনো ঠোঁটে তার শীর্ণ আশ্বাসের হাসি ফুটে উঠেছে। আর পাগলের ক্ষত-বিক্ষত কদর্য মুখখানিতেও কি করুণা বা মমতা! ছবিখানা এঁকে আমি খুশী হয়েছিলাম। পাগলের দৃষ্টিতে একটা মিস্টিক কিছু ফুটিয়েছি বলেই আমার বিশ্বাস!
ইংলণ্ডে গিয়েছিলাম, সেখানে একজিবিশনে ওখানা ছিল। একটি মেয়ে দেখে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, ‘Melting’ নাম দিয়েছ কেন? Beauty and the Beast নাম দিলেই তো পারতে। আমি বলেছিলাম, না, পাথর গলছে। দেখছ না, এই যে লোকটার গায়ের রঙে আমি পাথরের রঙ ফুটিয়েছি! পাথরের মত মানুষটা গলছে। ছবিটার প্রশংসা করেছিল অনেকে একেবারে কাছে মনে হবে পাথর। একটু দূরত্বে ভ্রম হবে, পাথর না মানুষ? দূর থেকে মনে হবে মানুষ কিন্তু বর্বর অথবা উন্মাদ।
ছবিটার দিকে তাকালে সুলতা। পাগল সম্পর্কে তারও কৌতূহল জেগে উঠেছিল। মনে হচ্ছিল, এই লোকটা যেন এদের সঙ্গে জন্ম-জন্মান্তরের সম্বন্ধসূত্রে জড়িয়ে রয়েছে।
সত্যই ছবিখানা ভাল। সুরেশ্বরের তুলির চাতুর্য বাস্তবকে লঙ্ঘন করে ছবিখানাকে ফুটিয়েছে অবাস্তব মাধুর্যে। তারই মধ্যে তার বক্তব্যকে প্রকাশ করেছে। লোকটা ঝুঁকে পড়েছে তার মুখের কাছে। তাতে পাগলের মুখে অন্ধকার বা ছায়া পড়বার কথা। কিন্তু সোফিয়ার মুখের রঙের আভাটিকে সে পাগলের ঝুঁকে-পড়া মুখের ওপর প্রদীপের আলোর মতো ফেলে প্রদীপ্ত করে তুলেছে। অথচ বাকী অঙ্গগুলিতে শেওলা-ধরা পাথরের রঙে তাকে অমানুষ অথবা অন্ধকারের মানুষ করে ফুটিয়েছে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সীমারেখায় একটু ঈযৎ সাদা আভাস। পাথর যেন সত্যই গলতে শুরু করেছে।
সুরেশ্বর তাকে ডাকলে—সুলতা!
—বল!
—ওটাতেই দৃষ্টিকে বেঁধে রেখো না। তারপর দেখ। রাত্রির পরমায়ু ফুরিয়ে আসছে। তার- পরের ছবিটা দেখ। ওই দেখ, বীরেশ্বর রায় কলম ধরে লিখছেন, কটি কথা লিখেই তিনি থেমে গেছেন। শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। একটু এগিয়ে গেলে নজরেও পড়বে-No.
অর্থাৎ সে আসে নি। ভবানী দেবীকে তিনি ফিরে পান নি সকালে। অথবা কোন একটি দীর্ঘ অবগুণ্ঠিতা নারী সন্তর্পিত পদক্ষেপে এসে দাঁড়ায় নি, জানবাজারের রায়বাড়ীর ফটকে।
পরের দিনের ডায়রীর পাতা আমিও ওই প্রত্যাশা করে উল্টেছিলাম। আমিও হতাশ হয়েছিলাম। লেখা ছিল, না। সে আসে নি। কল্পনা চিরকাল মিথ্যাই হয়। তারপর লিখেছেন, সারাদিন ভেবে ঠিক করেছি, কাশীতে লোক পাঠাব। পাঠাবার মত বিশ্বাসী লোক একমাত্র ছেদী সিং। কিন্তু সে বুড়ো হয়েছে। বয়স সত্তরের কাছে। কিন্তু ও ছাড়া এ কাজের ভার তো বিশ্বাস করে কারুর হাতে দিতে পারব না। ছেদী বারো বছর বয়সে ঢুকেছিল, বাবার বাচ্চা খানসামা বয় হিসেবে। তারপর আমার ভার পড়েছিল তার উপর। তখন সে ভর্তি জোয়ান। আমার মত সবল দুরন্ত ছেলেকে এদেশী চাকর সামলাতে পারত না। তাই ছেদীর উপর পড়েছিল আমার ভার। আমার পৈতের পর আমার খানসামা হয়ে এসেছিল মহেন্দর। আর ছেদী হয়েছিল আমার দারোয়ান, আমার সঙ্গে লাঠি নিয়ে মুরেঠা বেঁধে ফিরত। রবিনসনের কুঠী গিয়েছি, ছেদী সঙ্গে গিয়েছে, কোমরে তলোয়ার বেঁধে। যেখানে গিয়েছি, সে ছায়ার মতো ফিরেছে আমার সঙ্গে। আমার জন্যে প্রাণ সে দিতে পারত। আজ সে সত্তর বছরের বুড়ো, তবু সে আমাকে ছাড়ে নি। তার বাড়ি কাশীর ওপারে রামনগরের কাছে। আমি তাকে দিয়েছি অনেক। দেশে তার ক্ষতি হয়েছে। বাড়ীতে তার বেটা বেটী বউ। তাদের ছেলেপুলে হয়েছে। তবু সে আমাকে ছাড়তে পারে নি। জানবাজারের বাড়ীতেই থাকে। পেনশন দিয়েছি। ওকে পাঠাব। বছরে একবার সে বাড়ী যায়, দু মাস তিন মাসের জন্যে। সেই বাড়ী যাওয়ার নাম করেই যাক। কাশীতে এসে সে বিমলাকান্তের বাড়ী যাবে। দেখে আসবে সেখানে সে আছে কিনা! রাজা রাধাকান্ত দেবকে বিমলাকান্ত বলেছিল, এক ভগ্নীর কথা। ভগ্নী? তা ছাড়া বলবেই বা কি? হয়তো এক বাড়ীতে নাও থাকতে পারে। কারণ তার বাবাও নিরুদ্দেশ বা উদ্দেশহীন তার সঙ্গে সঙ্গেই। ছেদী পাকা খবর নিয়ে আসবে। তাকেই পাঠাব। অন্যকে এ খবর বলবার আমার সাহস নেই। তাকে পেলে তার সঙ্গে বোঝাপড়া আমি করব। কিন্তু লোকে তার নামে দুর্নাম দেবে, সে আমার সহ্য হবে না। রায়বংশের মাথা হেঁট হয়ে যাবে চিরদিনের জন্যে।
ছেদীকে ডেকে সব বললাম আজ সন্ধ্যায়। সে বললে—আপনে নিশ্চিন্ত থাকেন বীরাবাবু ভাইয়া; হামি বিলকুল খবর নিয়ে আসবে। তুরন্ত আসবে। এক রোজ বেফয়দা দেরী হামি করবে না।
রাণীগঞ্জ পর্যন্ত রেল হয়েছে। রাণীগঞ্জ পর্যন্ত ট্রেনে যাবে। তারপর গঙ্গার কোন ঘাটে গিয়ে নৌকো। উজান হলেও হেঁটে যাওয়ার চেয়ে শীঘ্র যাবে। আসবার সময় নিচের দিকে স্রোতের মুখে অনেক শীঘ্র হবে। মোটমাট মাস চারেক লাগবে। কিন্তু আমার ধৈর্য যেন থাকছে না। চার মাস দীর্ঘ সময়।
আজ সন্ধ্যেটাই কাটছে না। একা বসে আছি। ছেদীকে টাকা-কড়ি দিয়ে বিদায় করে লিখছি, আর ভাবছি। চার মাস!
সোফিয়ার অসুখ। সকালবেলা ওর লোক এসেছিল, বললে —সোফিয়া ভাল আছে। বিপদ কেটেছে। কিন্তু খুব দুর্বল। উঠে বসতেও পারে না। জোঁক বসিয়ে অতিরিক্ত রক্ত ক্ষয় হয়েছে। কালো মুখখানা কাগজের মতো সাদা দেখাচ্ছিল। তার উপর এত বড় বিকারটা গেল। আশ্চর্য! তাহলে তো ওই সন্ন্যাসীর কোপেই এমনটা হয়েছিল। সন্ন্যাসীর কৃপাতেই তো সারল। সন্ন্যাসীর আশ্বাসে চোখ মেললে। নিষ্প্রভ চোখে যেন প্রদীপ জ্বলল। আমার চোখের উপর ভাসছে। আর ওই বিচিত্র পাগলের মুখে কি আশ্চর্য করুণা দেখলাম! আমার কাছে একটা বিস্ময়ের মত মনে হচ্ছে। ভাবছি, এদের ক্রোধ হয় যত সামান্য অপরাধে, আবার কি অফুরন্ত আশ্চর্য দয়া এরা ঢেলে দেয় মানুষের দুঃখ দেখে।
সোফিয়ার লোকটা বললে—সারারাত্রি পাগল সোফিয়ার মুখের কাছে ঠিক তেমনি করে তাকিয়ে বসে ছিল। মধ্যে মধ্যে শুধু বলেছে, ভাল হয়ে যা। যা। ভাল হয়ে যা। আ-হা-হা-রে! বলেছে, নাকি ভাল হয়ে যাবে আজ!
অবিশ্বাস্য কথা। সোফিয়ার সুস্থ সহজ হতে বেশ কিছুদিন লাগবে। তবে এরা হয়তো সব পারে। বেচারী সুস্থ হোক। সম্পূর্ণ সুস্থ হোক। তবে আজ সোফিয়া থাকলেই কি ভাল লাগত? বোধ হয় লাগত না। মনে হচ্ছিল, এখন মনে মনে নিজেকেই জিজ্ঞাসা করছি, আর কাউকে ডাক দেব? আমার নাম শুনলে নিশ্চয় আসবে। কিন্তু তাও ভাল লাগছে না। না, ভাল লাগছে না।
জীবনে যেন একটা ক্লান্তি এসেছে ওতে। হ্যাঁ, ক্লান্তি এসেছে। আজ দীর্ঘদিন এতেই ডুবে ছিলাম। নদীর মধ্যে কুমীর যেমন ডুবে থাকে, তেমনি করে ডুবে ছিলাম। কীর্তিহাটে মদ্যপান করে উন্মত্ত হয়ে থাকতাম। নিষ্ঠুরতম মানুষ হতে চেয়েছিলাম, কিন্তু ব্যভিচার করিনি। শিকার করেছি। মানুষকে নির্যাতন করেছি। কি করেছি সব মনেও পড়ে না। খাতাখানা উল্টে দেখছি। সাত বছর আগে সে যেদিন নিরুদ্দেশ হল, তার পরদিন লিখেছিলাম—Am I going mad? Yes, it is madness. It is coming.
তারপর আর লিখিনি; কলকাতা আসবার আগে রবিনসনের লক্ষ্যভ্রষ্ট এক বাঘিনীকে মেরে তাকে মৃত্যুমুখ থেকে বাঁচিয়েছিলাম, সেই ঘটনাটা লিখেছি। তারপর কলকাতায় এসেছিলাম নতুন মানুষ হতে। তখন থেকে লিখছি। কিন্তু নতুন জীবন আরম্ভ করেও পারি নি। সোফিয়াকে পেয়ে আশ্চর্য ভাল লেগেছিল। মনে পড়েছিল, দাদার বিয়ের আসরে ওর গান আধ-শোনা করে উঠে গিয়েছিলাম, তারই ডাকে। তাই মনে হয়েছিল, ওর গানই শুনব এবার যতদিন বাঁচি। কিন্তু তাতেও যেন অরুচি এসেছে। রাজাবাহাদুরের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর মনে নতুন স্বাদের সাধ জেগেছে। তারপর এই খবর। জগদ্ধাত্রী-বউদি দিলেন এই চিঠি। চিঠিতে বেনারসের ছাপ আছে। আর সোফিয়াকে নিয়ে মেতে থাকবার কল্পনাও ভাল লাগছে না। মনে হচ্ছে, সোফিয়ার অসুখ হয়ে একটা মুক্তি পেয়েছি। মদ ভাল লাগছে না। থাক, সোফিয়া কিছুদিন বিশ্রাম নিয়ে সুস্থ হোক। আমি তার কথা ভাবব। আর নতুন মানুষ হবার চেষ্টা করেও দেখি। রাজাবাহাদুরকে ভাল লেগেছে।
সুরেশ্বর বললে—বীরেশ্বর রায়ের জীবনে সত্যই তখন একটা নতুন স্বাদের আকাঙ্ক্ষা জেগেছিল। সোফিয়ার কথা আর ভাবেন নি। সে সেরে উঠছে। নতুন কাউকেই ডাকেন নি। ভাবছিলেন-কিভাবে শুরু করবেন নতুন জীবন।
সঙ্গে সঙ্গে কাজও যেন কেউ যুগিয়ে দিয়েছিল। যুগিয়ে দিয়েছিল জমিদারী। দিন-তিনেক পরেই কীর্তিহাটের নায়েব ম্যানেজার গিরীন্দ্র আচার্য মহিষাদল স্টেটের কাছ থেকে ষোল আনা তৌজি পত্তনী নেওয়ার ব্যবস্থা করে তার কাগজপত্র নিয়ে এসে পৌঁছেছিলেন। পত্তনী বন্দোবস্তীর পাট্টা কবুলতি, লাট ও তৌজি দিগরের একজায় কাগজপত্র নিয়ে বোঝাই দুটো বড় প্যাটরা। প্রথমটা বীরেশ্বরের ভাল লাগে নি। বলেছিলেন-ওসব আর আমি কি দেখব বলুন। আমার ওতে তো আগ্রহ রুচি বিশেষ নেই। আপনি দেখেছেন তো।
গিরীন্দ্র বলেছিলেন—না, তোমাকে একবার দেখতে হবে বইকি। দেখার প্রয়োজন আছে। পাট্টা কবুলতির বয়ানে দুটো জায়গায় আমার সঙ্গে মতের ফারাক হয়েছে। সে দুটো দেখ। আর—
অসহিষ্ণু হয়ে বীরেশ্বর প্রশ্ন করেছিলেন—কি সে দুটো?
প্রথম ওঁরা দলিলে ‘দোরবস্ত হক-হুকুক’ লিখেই সেরে দিতে চান, আমি বলেছি-তা হবে না, ওসব মহলওয়ারী স্বত্বের নাম যথারীতি লিখে দিতে হবে, পাতামহল, কাষ্ঠমহল, কয়লামহল, মৌজামহল, হাট-ঘাট-গঞ্জ, নিমকমহল আদি সহ দোরবস্ত হুকুক কথাগুলি লিখতে হবে। তা ওঁরা বলেছেন—নিমকমহল তো লেখাই চলবে না, কারণ ও তো সরকারী খাস; খালারি বন্দোবস্তি যা করেন, সে তো কোম্পানী করেন, ও কোম্পানীর একচেটে। আমি বলেছি আমরা তা স্বীকার করব কেন দলিলে। এই তো লাখরাজ নিয়ে মামলায় বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর প্রিভি কাউন্সিলে জিতে লাখরাজ টিকিয়ে দিলেন। কে জানে নিমকমহল নিয়ে মামলা-মোকদমা করলে প্রিভি কাউন্সিলের কি রায় হবে? আবার ডৌল ধার্য করবার সময় পাতামহল, কাষ্ঠমহল, কয়লামহলের আয় তার সঙ্গে যোগ করতে চাচ্ছেন। বলছেন, জঙ্গলমহলগুলোতে পাতা বন্দোবস্তিতে একশো-দেড়শো পাই ও কয়লামহলে কাঠকয়লায় আয়—তাও দেড়শো-দুশো, কাঠ থেকে আয় তো মোটা—মানে দু হাজার আদায়ী ডৌল হলে পাঁচশো টাকা। এই সবের আয় চাপাতে চাচ্ছেন। করছেন সবই ওঁদের ম্যানেজার। মানে তো বুঝতে পার। আমি বলেছি, সে অবশ্যই হবে। যেমন প্রচলন আছে—নায়েবের প্রাপ্য, গোমস্তাদির প্রাপ্য, সে তো দিতেই হবে। দেব। তা—মানে রাঘব বোয়ালের খাঁই। আগেভাগেই দাও আর কি! এ তোমাকে দেখতে হবে। যেতে হবে, রাজাবাহাদুরের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে হবে। রাজাবাহাদুরের অভিমান রয়েছে, দেখলাম। মানে ওঁর ইচ্ছে, তুমি পত্তনী নিচ্ছ, তুমি ওঁদের কাছে যাবে, বলবে। এই আর কি—
বীরেশ্বর রায় এসব বোঝেন। ভাল করেই বোঝেন। জমিদারীর আয়—তিল কুড়িয়ে তাল; বাদশা-নবাবদের আমলে সে এক কাল গেছে। এই তো বলরামপুর জানপুর থানায় খয়রারাজারা সতেরোটা পরগণায় নবাব দপ্তরে খাজনা দিত বছরে বারোশো টাকা, তাও কোন বছর দিত, কোন বছর দিত না; ইংরেজরা প্রথম এসেই গ্রাহাম সাহেবের আমলে সেই খাজনা করেছে বাইশ হাজার টাকা। তারপর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় সে খাজনা সতেরো পরগণার পাই-পয়সা আদায় জুড়ে মোট আদায়ের একশো ভাগের নব্বুই ভাগ ধার্য করেছে।
হিসেব করেছেন তাঁরই ঠাকুরদা। কি করবেন, হুকুম কোম্পানীর, আর তদারক দেওয়ান রায়রাইয়া সিংহজীর।
মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় নাকি লিখেছিলেন—পুত্র অবাধ্য, দরবার অসাধ্য, ভরসা কেবল দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ।
বর্ধমানের মহারাজা দেওয়ানবাহাদুরের মাতৃশ্রাদ্ধে আসেন নি বলে তাঁর জমিদারীর উপর শতকরা নিরেনব্বুই টাকা কালেক্টারী খাজনা ধার্য হয়েছে।
শেষ পর্যন্ত অষ্টম আইনে বর্ধমান এস্টেট বেঁচেছে। লোকে বলে বর্ধমানের মহারাজার বাঁচবার জন্যে অষ্টম আইন সৃষ্টি করেছিল কোম্পানী সরকার। শুধু বর্ধমান কেন, গোটা বাংলাদেশের রাজা জমিদারেরা বেঁচেছে পত্তনী আইনে। ইংরেজদের আমলে পাই-পয়সার কড়া হিসেব; বেনে হয়েছে রাজা। বাদশাহী আমলে যে আমীরী চলেছে, মাইফেল চলেছে, দানপত্র চলেছে, সে আজ অচল, চলতে পারে না। আজ বনে যে শালপাতাওয়ালারা পাতা নিয়ে শালপাতা তৈরী করে, তার উপর জমা ধার্য করতে হয়েছে জমিদারকে। বনে আগুন লেগে কাঠকয়লা হয়, স্বর্ণকারে কর্মকারে কেনে, নুনের খালারীতে লাগে, তারও জমা ধার্য হয়েছে। নদীর ঘাটের জমা, হাটের জমা, নানান জমা করে তাই থেকে আয় বাড়াতে হয়েছে এবং হবেও।
আবওয়াবও আদায় করতে হয়। আবওয়াব অবশ্য চিরকাল আছে। সে বাদশাহী নবাবী আমল থেকে। ছেলের বিয়ে, মেয়ের বিয়ে, ঠাকুরপ্রতিষ্ঠা, পিতৃশ্রাদ্ধ এতে আদায় হয়, এ তাঁর মতে অন্যায় নয়। তবে মাথট, বছর বছর একটা না একটা চাঁদা, এটা অন্যায়। দক্ষিণের জমিদারদের নাম করবেন না, অন্ন জুটবে না, মুখের অন্ন বরবাদ হবে, গারদ মাথট আদায় করে নাম কিনেছেন বটে। কুমোররা হাঁড়ির জন্যে মাটি নেয়, তার জন্যে জমা আদায়টা তাঁর ভাল লাগে না। মাটি, জল। এ দুটোর উপর—না-না, ওটা ঠিক নয়।
দলিলের খসড়া দেখতে দেখতেই ভাবছিলেন তিনি। ওদিকে গিরীন্দ্র আচার্য ষোল মৌজার ডৌল-জমার হিসেব, পতিতের পরিমাণ, তার মধ্যে ‘রগবা’ মানে আবাদযোগ্য পতিতের হিসেবের কাগজ সাজিয়ে রাখছিলেন থাকে থাকে।
রায় দলিলের খসড়া দেখে বললে–আপনি যা বলেছেন, তাই ঠিক, ওসবের স্পষ্ট উল্লেখ থাকা দরকার। এ তো সব দলিলের বাঁধা বয়ান। এ মহল, ও মহল, হাট-ঘাট—গোলাগঞ্জ, খানা-খন্দক, খাল-বিল, দোরবস্ত হক-হকুক, ঊর্ধ্ব-অধঃ- যে যে স্বত্বে আমি স্বত্ববান, এ লিখতেই হবে। না হলে এর জন্যে পরে হাঙ্গামা হতে পারে। যে কেউ বলতে পারে, জমিদার এ রাইট দেয়নি পত্তনীদারকে। দোরবস্তু হক-হুকুকের মানে তো ঠিক হয় না। পুকুর কাটাতে, কুয়ো কাটাতে না হয় লোকে জমিদারের হুকুমনামা নেয়। কিন্তু ঘুড়ি ওড়াতে তো হুকুমনামার দরকার হয় না, কোন জমিদার তা দাবীও করে না। ওসব প্রত্যেক আইটেম লেখা থাকা উচিত। ঊর্ধ্ব শব্দ লেখা থাকলেও এসব ক্ষেত্রে তার মানে নেই। তবে নিমক-মহল সম্বন্ধে লিখতে পারেন, “সরকারী আইনগত পরিবর্তন মত জমিদারের যা প্রাপ্য সেই স্বত্ব আদি”। বুঝেছেন—তাহলে ওঁদের আপত্তির আর কিছু থাকবে না।
—সেও আমি বলেছি। যা বলবার তা বলতে ফাঁক আমি রাখিনি। তবে আসল কথা টাকা। তাও মনিবের স্বার্থে নয়। আপন আপন পেট ভরণের জন্যে। তা নইলে এতবড় রাজ-এস্টেটের এই অবস্থা হয়। খাজনা আদায়ই করে না গোমস্তারা। ওই ঘরে বসে মাইনে নেয়, যা পায় নিয়ে আসে; কিছু দেয়, কিছু ট্যাকবন্দী করে। বকেয়ার কাগজ দেখে না। পঞ্চাশ বছরের খাজনা বাকী চলে আসছে। অবশ্যি খাজনা কম, মুসলমান প্রজা। এছাড়া বিশ-পঁচিশ-তিরিশ বছর প্রচুর। আট বছর, দশ বছর তো হামেশা বাকী। ষোল মৌজাতে বাকির অঙ্ক দু-লাখের কাছাকাছি। সব নগদ খাজনার মহাল। উটবন্দী ফসলমুখী কাটা খামার চলনের মহাল আমি নিইনি। বলেছি ওসব চলবে না। বরং সাজা খাজনার তৌজি বেছে নিয়েছি। আদায় একটু কষ্ট বটে। তা লাঠি থাকলে আদায় বাপ-বাপ বলে হবে।
বীরেশ্বর রায় বাকী জায়ের কাগজের থাক টেনে নিলেন।
আচার্য বলেই চললেন—বাবা, এই নিয়ে আমার সঙ্গে বনল না। আমাকে ছোট দেওয়ান করে নিয়ে এল, বুড়ো দেওয়ান বললেন, দেখ, অক্ষম হয়েছি, তুমি বাপু ইংরিজী-টিংরিজী জান, আর হাল-আমলের লোক, দেখেশুনে চালাও। চালাচ্ছিলাম। কাগজপত্র দেখে চক্ষু চড়কগাছ। এ কি ব্যাপার? এত বাকী? এ তো হাল আইনে সব তামাদি। চার বছর খাজনা, এক বছরের খাজনা সুদ, এই পাঁচ বছরের খাজনা ছাড়া তো সব জলে গিয়েছে। তা বুড়ো দেওয়ান বললেন, না না। তামাদি নেই। আমাদের এস্টেটে সুদও নিই না আমরা, প্রজারা তামাদিও বলে না। বলবে না। বুড়ো দেওয়ান বলেছিলেন, সে প্রাণ গেলেও বলবে না। আমি সেই দিনই বলেছিলাম, দেওয়ানজী, মুখে না হয় বলবে না, বললে না। কিন্তু বললেও না, আদায়ও দিলে না, দেনদারও মরে গেল, পাওনাদার গেল। তাহলে হলটা কি? বললেন, এর ছেলে দেবে, ওর ছেলে নেবে। বর্গী-হাঙ্গামার সময় একশো বছর আগে গোয়া থেকে কতকগুলো হারমাদ গোলন্দাজ আনা হয়েছিল, গড়ে কামান বসানো হয়েছিল, তারা বসে আছে; কি করবে, কাজকাম তো এখন নাই। তাদের জায়গা-জমি দিয়ে, গেঁয়োখালির কাছে বাস করিয়েছিলেন রাজা আনন্দলাল উপাধ্যায়। তারা এক গলগ্রহ, গোটা দুটো মৌজা জুড়ে বাস করছে। খাজনা না, পাতি না; কাজও নাই, কামও নাই। কটা-কটা চোখ, কটা-কটা, রঙ। বেঁকা-বেঁকা কথা মধ্যে মধ্যে আসে, হামলা করে, খানে দিজিয়ে। ভুখে মরছে। ধর উপাধ্যায়দের বংশই নেই অবীরা রানী জানকীবাঈ গুরুবংশ, গর্গদের জগন্নাথ গর্গকে দিয়ে গেলেন গদী। তিনি মারা গেলেন, নাবালক ছেলে রামনাথ গর্গকে রেখে সৎ-মা ইন্দ্রাণী তার গার্জেন ছিলেন। তারপর রামনাথ গর্গ মারা গেলেন; তিনিও নিঃসন্তান—রানী বিমলা দেবী সতী হলেন আগরপাড়ার চরে; রানী ওই সতী হবার সময়ে একটা কাগজে লিখে এই লক্ষ্মণ প্রসাদকে গদী দিয়ে গেলেন। দোষই বা কাকে দোব। এক-এক মন্দির আছে-যার চূড়ো যতবার কর ভেঙে পড়বেই, এ এস্টেটেরও তাই। অল্পবয়সে যায়। রানী-মায়েরা পোষ্য নেন। নাবালক ছেলের গার্জেনী করেন। কাজেই বংশে মহাভয় ঢুকে আছে, এতে পাপ অর্শাবে, ওতে পাপ অর্শাবে। এ করতে নাই, ও করতে নাই। এই সুযোগে এরা এসে খেতে চাইত। হাঙ্গামার ভয় দেখাত। আর নিয়ে যেত খাবার। অবিশ্যি সবাই তা নয়। জন-বিশ-পঁচিশেকের একটা দল ছিল। নদীতে ডাকাতি করত। একবার-যেবার তোমার বজরার ওপর হামলা করবার চেষ্টা করেছিল। তা পারেনি—
বীরেশ্বরের মনে পড়ে গেল। তিনি বন্দুক চালিয়েছিলেন। ভবানী বন্দুকে বারুদ ঠেসে ঠিক করে দিয়েছিল। কাগজ থেকে একবার মুখ তুললেন তিনি। তাকালেন সামনের বারান্দার দিকে।
আচার্য বলেই চলছিলেন—তোমার বন্দুকের গুলিতে একটা গোয়ান মরেছিল বোধ হয়। তাদের আমিই ও এলাকা থেকে তাড়িয়েছিলাম। হুজ্জোত কম হয়নি। তবে দুটো দল হয়ে গিয়েছিল। যারা ভাল লোক, তাদের জমিজমা দিয়ে, হাল-গরুর খরচ দিয়ে চাষীবাষী করিয়ে ওদের দিয়েই এ-বেটাদের খেদিয়েছিলাম। কোম্পানী সরকার খুব সাহায্য করেছিল। বেটারা ও-গ্রাম থেকে পালিয়ে একেবারে গাং পার হয়ে চব্বিশ পরগণার জঙ্গলে আড্ডা গেড়েছিল। এখন শুনি হিজলীর সেকালের নবাবদের বংশের এক পীরসাহেব আছেন, তিনি নাকি তাদের আশ্রয়-টাশ্রয় দিয়েছেন। বাকিরা এখন বেশ গেরস্ত হয়ে গিয়েছে। তারা বেশ ভদ্র আর এদেশী হয়ে গিয়েছে। তা আমি ওসব তৌজি নিইনি। ও—ওঁদেরই থাক।
বীরেশ্বর রায় তৌজির পর তৌজির বিবরণের কাগজ উল্টে দেখছিলেন। গিরীন্দ্র আচার্যের বাক্যস্রোতের ঝরঝর শব্দে তাঁর মন আকৃষ্ট হয়নি; মনঃসংযোগে বাধার সৃষ্টিও করতে পারেনি। কিন্তু ওই হলদীর মোহনায় তাঁর বজরার উপর গোয়ানদের হামলার কথা বলতেই মনটা চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। কিছুক্ষণ অন্যমনস্কভাবে বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি। বারান্দায় বসে টানা পাখাওয়ালাটা পাখা টানছে। চাকর মহেন্দ্র দরজার গোড়ায় বসে আছে। কথাবার্তায় মৃদু গুঞ্জন উঠছে বারান্দার কোনখানে। হুকাবরদার হাত-পা টেপার হিন্দুস্থানী খানসামাটা বোধ হয় গল্প করছে।
এদিকে বলেই চলেছেন আচার্যি ম্যানেজার, আমি থাকলে আমার পরামর্শমতো চললে এ অবস্থা হত না। আমি সোজা করেও সব এনেছিলাম। তা ওই তো বললাম, একদিকে এস্টেটের কর্মচারীদের আঁতে টান পড়ল। তারা নাবালক আর পোষ্যপুত্রের আমলে চোখে ধুলো দিয়ে খাচ্ছিল, তা বন্ধ হল, পাঁচখানা করে লাগাতে লাগল। ওদিকে প্রজারাও এসে কাঁদতে লাগল। আর মালিকরা ভয় পেলেন এই তো এ বংশে পোষ্যপুত্রের পর পোষ্যপুত্র চলছে; মালিক মারা যাচ্ছে অকালে। এইসব চোখের জলে অকল্যাণ হবে; ভয়ে আমাকে বললেন—এসব চলবে না আচার্যি-না, না। প্রজার ওপর এমন কড়াকড়ি লোকে শাপশাপান্ত করছে। আমি সেই দিন জেনেছিলাম এর আর প্রশ্ন নাই—একদিন-না-একদিন—
আবার বাধা দিলেন বীরেশ্বর রায়। তিনি আবার কাগজে মন দিয়েছিলেন। এসবের একটা নেশা আছে। এ যে বোঝে তার মন মিষ্টান্নের ওপর মক্ষিকার মত বসলে নড়ে না। তাড়িয়ে দিলেও উড়ে আবার একটা পাক দিয়ে এসে বসে যায়। বীরেশ্বরের মনও ওই মক্ষিকার মত জমিদারী বিবরণের মিষ্টান্নের উপর আবার এসে জমে গিয়েছিল। একখানা মৌজার বিবরণের পাতা উল্টে পরের পাতায়—মাথায় মৌজার নামটা দেখেই বললেন মৌজা বীরপুর! মণ্ডলান তৌজি!
আচার্য সোজা হয়ে বসলেন। নিজের পায়ের উপর নিজে হাত বুলিয়ে একটু দুলতে দুলতে বলতে লাগলেন, হ্যাঁ বাবা মণ্ডলান তৌজি। মণ্ডল গোপাল সিং। ও আমি যেচে নিয়েছি বাবা। কত্তার সামনে চেয়ারে বসে সেই “আমরা ছত্তিরি রায়বাবু” বলে মোচপাকানো আমার মনে আছে। ওর সঙ্গে সে আমলে মামলা করে জিতে আমার মনের সুখটা হয়নি। এবার ওর সঙ্গে একবার পাঞ্জা লড়ব।
কথাটা মনে পড়ল বীরেশ্বর রায়ের। তিনি শুনেছিলেন, ব্যাপারটা তাঁর সামনে ঘটেনি। বীরপুর মৌজার পাশেই রায়দের গগনপুর লাটের এলাকা। দুই এলাকার মাঝে একটা জঙ্গল। সেই জঙ্গলের যে অংশটা রায়বাবুদের, সেই অংশ থেকে গোপাল সিংয়ের লোকেরা কখনও জবরদস্তি, কখনও চুরি করে কাঠ কেটে নিয়ে যেত। মহিষাদল এস্টেটের মণ্ডলান তৌজি বীরপুর। মণ্ডল গোপাল সিং, জাতিতে সে ছত্রি, এককালে পাইকদের সর্দার ছিল, মণ্ডলান আদায় যেখানে, সেখানে জমিদারের সঙ্গে জমিদারীর সম্পর্কে বলতে গেলে না-সম্পর্ক। জমিদার তৌজির খাজনা পায় মণ্ডলের কাছে। বছর বছর বন্দোবস্ত কোথাও। কোথাও দু’-চার বছর অন্তর। মণ্ডল ব্যক্তিটিই সর্বেসর্বা। সে তৌজির খাজনা জমিদারকে দিয়ে জমিজমা ইচ্ছেমত প্রজার সঙ্গে বন্দোবস্ত করে। যাকে ইচ্ছে হয় তাকে জমি দেয়। ইচ্ছে হলে উৎখাত করে। মোট কথা, আইন অনুসারে স্বত্বের জোরে জমিদার না হয়েও সেই জমিদার তৌজি একবার মণ্ডলান আদায় বন্দোবস্ত করলে, আর সে মণ্ডলকে উচ্ছেদ করা খুব কঠিন। মহিষাদল এস্টেটে কথাটা জানানো হয়েছিল। সোমেশ্বর রায় লোক পাঠিয়েছিলেন। দুই এস্টেটে কোন মনোমালিন্য ছিল না। মহিষাদল চিঠির উত্তরে গোপাল সিংকে পাঠিয়েছিলেন সোমেশ্বর রায়ের কাছে।
সোমেশ্বর রায় কাছারী-ঘরে বসেছিলেন। তিনি বসতেন ছোট একটা চৌকিতে কার্পেট বিছানো গদিতে। পিছনে থাকত মোটা মখমলের তাকিয়া। সামনে একপাশে থাকত খানকয়েক চেয়ার-কুর্শী। অন্যদিকে থাকত একটু নিচু তক্তায় শতরঞ্জির উপর চাদর। ওর উপর বসতেন ব্রাহ্মণ কায়স্থ ইত্যাদি সদগৃহস্থ প্রজারা। সাধারণ প্রজাদের জন্য মেঝের উপর মাদুর- কম্বল বিছানো থাকত। কুর্শীর ব্যবস্থা ছিল বিশেষ লোকের জন্য। যেমন মিয়া মোকাদেম কিম্বা দারোগা বা আদালতের নাজির-টাজির। নানান কাজে এঁদের আসতে হত। মধ্যে মধ্যে বুড়ো রবিনসন এবং পাদরী হিলসাহেব এলে বসত। আর একদিকে একটা চৌকিতে বসত নায়েব-ম্যানেজার।
গোপাল সিং দেখা করতে এসে কপালে হাত ঠেকিয়ে নমস্তে রায়বাবু বলে সটান গিয়ে ওই একখানা কুর্শীতে চেপে বসেছিল।
সোমেশ্বর রায় অবশ্যই ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু নিজে মুখে কিছু বলেননি। বলেছিল আচার্য ম্যানেজার। ওসব কুর্শী সাহেব-সুবা দারোগা নাজীরের জন্যে গোপাল সিং। মণ্ডল প্রজার জন্যে নয়। ওই—ওই
তিনি দেখাতে গিয়েছিলেন, মেঝের উপর বিছানো সতরঞ্জি কম্বলের বিছানা, কিন্তু সোমেশ্বর রায় ভদ্রতা করে বলেছিলেন, এই যে তক্তাপোশের উপর ফরাস রয়েছে সিং, এইখানে বস।
গোপাল সিং বলেছিল, আমি ছত্রি রায়বাবু। বাংগালী নই। এককালে আমার দাদো ছিল মনসবদার। দারোগা নাজীর লোকের চেয়ে ছোট আছি না। বেশ বসেছি আমি। বলেন—কিসের লেগে তলব!
সোমেশ্বর রায় বলেছিলেন, আগে জল খাও গোপাল, তারপর হবে কথা। তাড়াতাড়ি কিসের? আচার্য, সিংকে জল খাওয়াও।
জল খেয়ে গোপাল এসে বলেছিল, এখন বলেন কি কথা?
সোমেশ্বর বলেছিলেন, আমি তো তোমাকে তলব পাঠাইনি গোপাল। তুমিই বলবে কথা কি।
—আমার রাজাসাহেব বলেন, কীর্তিহাটের রায়বাবুর কিসব কথাবার্তা আছে, তুমি যাও গোপাল সিং শুনে এস। ফয়সালা করে এস।
—কথাবার্তা বীরপুর সীমানার জঙ্গল নিয়ে। তা তুমি তো মণ্ডল—তা নিয়ে তোমার সঙ্গে কথাবার্তা কি? সে রাজাবাহাদুরের এস্টেটের সঙ্গে। হবে তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা।
—তবে সেই করবেন। সেই ভাল। তারপর হেসে বলেছিল, এক কাজ করেন রায়বাবু, বীরপুরের সীমানা নিয়ে গোল লাগছে আপনার গগনপুরের সীমানার। গগনপুরে আমাকে একটা আপনার খাস জোত দিয়ে দেন। হাঁ, সেলামি কিছু দিব। আর গগনপুর ওই বীরপুরের মতুন আমাকে মণ্ডলান বন্দোবস্ত করুন। সব মিটে যাবে বাবা। কুনো গোল থাকবে না।
আচার্য রুখে উঠেছিলেন। কিন্তু সোমেশ্বর রায় ইঙ্গিতে নিষেধ করেছিলেন। এরপর আরম্ভ হয়েছিল মামলাপর্ব। মহিষাদলের সঙ্গে নয়। চুরি, রাহাজানি, চার্জ দিয়ে বীরপুরের যারা গোপাল সিংয়ের চ্যালাচামুণ্ডা, তাদের উপর নালিশ। মামলার পর মামলা, পাঁচ বছর মামলা চলার পর গোপাল একটা মিটমাট করেছিল। তাও মহিষাদলের রাজাবাহাদুরের অনুরোধে মিটমাট করেছিলেন সোমেশ্বর রায়।
বীরেশ্বর রায়ও সোজা হয়ে বসলেন। সমস্ত বিষয়-ব্যাপারটা মিষ্টান্নের উপর গোলাপজলের ছড়া দেওয়াতে সৌরভযুক্ত বা লবণাক্ত ব্যঞ্জনে লঙ্কার গুঁড়ো ছিটা দেওয়ার মত ঈষৎ ঝাল হয়ে অধিক মুখরোচক হয়ে উঠল। বললেন, ভাল করেছেন। প্রয়োজন ছিল। এটা অবহেলা করে এসেছি আমরা। বাবা তো এরপর বেশী দিন বেঁচে ছিলেন না। যে কিছুদিন ছিলেন, তখন তাঁর জামাতা দেখাশুনা করেছে। আমি তখন কলকাতায়। তারপর আমি হাতে নিয়েছি সম্পত্তি, অবহেলা আমারই বলতে হলে। ভাল করেছেন।
—নিশ্চয়। তোমরা ভুললে আমি ভুলব কেন? যে চেয়ারখানায় বসেছিল, সেখানা আমার চিহ্নিত করা আছে বাবা। আমি ওকে হাঁটু ভাঙিয়ে ঘোড়ার মত বসাব, বসিয়ে পিঠের ওপর চেয়ারখানা লাগাব, আর চেয়ারের ওপর একমুণে একটা পাথর চাপিয়ে দেব। তার ওপর একটা বাঁদর। হাঁ, যখন বীরপুর বাছাই করি, তখন থেকে ভেবে ভেবে আমি কি করব তা ঠিক করে রেখেছি।
তারপর বললেন, শুধু বীরপুর নয়, পাতা উল্টাও, দেখ, শালমুঠা-আঁচলপাড়াও বেচেছি। ভুবন মাইতি আমাদের এলাকা থেকে উঠে গিয়েছে, সব বিক্রী করে বলে গিয়েছে—রায়বাবু- দিগে খাজনা আমি দোব না। আর সর্বানন্দ ঘোষ উঠে গিয়ে বাস করছে আঁচলপাড়ায়। তোমার আমলেই একটা ফৌজদারী মামলায় আমাদের চাপরাসীর জরিমানা করিয়ে ভয়ে পালিয়ে গিয়েছে। এ দুজনের সঙ্গেও মোকাবেলা হবে, দেখা যাবে এরপর কোথা যাস বাছাধনেরা!
একটু হাসলেন বীরেশ্বর রায়। ও দুজনের ব্যাপার সামান্য। বলতে গেলে কিছুই নয়। কিন্তু আচার্য তা ভোলেননি। রায় কাগজ উল্টে গেলেন।
এরই মধ্যে অত্যন্ত করুণ বিনীত ভঙ্গীতে এসে দাঁড়িয়েছিল মহেন্দ্র চাকর। কিছু নিবেদন আছে তার।
রায় মুখ তুলে প্রশ্ন করেছিলেন—কি?
—আজ্ঞে ম্যানেজারবাবুর খাবার—।
—এর মধ্যে খাব কি রে?—বলেছিলেন আচার্য। তারপরই ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলে- ছিলেন, আরে বাবা, এ যে বারোটা বাজে। ওঃ! একেবারে বুঝতেই পারি নাই, রাত হয়েছে। তাহলে আজ উঠি বাবা। কাল আবার হবে। ওঃ, তোমার সব ব্যাঘাত করে দিলাম। বলে তিনি উঠে পড়লেন।
ব্যাঘাত করে দিলাম অর্থে মদ্যপানের কথা বলছেন আচার্য। কিন্তু মদ্যপান আজ ক’দিনই তিনি করেননি।
তারপর একনাগাড়ে এই দেড় মাসের উপর সময়টা তিনি বিষয় নিয়েই আছেন। বিষয়ী ঘরের ছেলের বিষয়ে যে স্বাভাবিক প্রীতি ও আসক্তি, তা সুযোগ পেয়ে জিহ্বা বিস্তার করে জেগে উঠেছে। ডৌল কষেছেন, পতিতের হিসেব করেছেন, কোথায় নদীতে বাঁধ দিতে হবে, কোথায় কয়েকটা বাঁধ কাটাতে হবে, তাতে কত পতিত আবাদ হবে এবং এই ডৌল জমার উপর কত বৃদ্ধি কোথায় সম্ভবপর হবে—এই নিয়ে মস্ত একখানা খাতা তৈরী করে ফেলেছেন। দলিল নিয়ে রাজাসাহেবের কলকাতায় অ্যাটর্নীর বাড়ী গিয়েছেন। নিজের অ্যাটর্নীর সঙ্গে পরামর্শ করেছেন—পত্তনী মৌজাগুলি নিয়ে আয়বৃদ্ধির পথ আবিষ্কার করেছেন।
ষোলখানা পত্তনী মৌজার ডৌল কুড়ি হাজার পাঁচশো বাইশ টাকা এগারো আনা দশ গণ্ডা। সরকারী রেভেন্যু আঠারো হাজার টাকা পাঁচ আনা দশ গণ্ডা। সরঞ্জামী অর্থাৎ আদায় খরচা শেষ পর্যন্ত স্থির হয়েছে শতকরা আড়াই টাকা হিসেবে পাঁচশো দশ টাকা। লাভ ছেড়ে দিতে চেয়েছেন নিট মুনাফার শতকরা পঁচিশ টাকা। এই লাভের টাকার উপর দশগুণ টাকা সেলামী ধার্য হয়েছে অর্থাৎ ষোলআনা মৌজায় রেভেন্যু এবং জমিদারের মুনাফা বাদ দিয়ে লাভ থাকবে পাঁচশো টাকা। তা হোক। আচার্যের সঙ্গে পরামর্শ করে যে মতলব করেছেন বীরেশ্বর রায়, তাতে এই পাঁচশো টাকা লাভ আগামী বছরের মধ্যে পাঁচ হাজারে গিয়ে দাঁড়াবে। কুড়ি হাজার পাঁচশো টাকা আদায়ের উপর টাকায় সিকি বৃদ্ধি করলেই পাঁচ হাজার টাকা আয় বাড়বে। এর সঙ্গে পাতা, কাঠকয়লা, কাঠমহলের জমা আছে। ষোলখানা গ্রামের চারখানাতে হাট আছে এবং ছয়টা খেয়াঘাট আছে। তাতেও সমস্ত জুড়ে পাঁচশো থেকে হাজার টাকা আয় বাড়বে। এসব জমা মহিষাদল এস্টেট আদায় করতেন না। গোমস্তারাই কিছু কিছু নিয়ে বিলি-ব্যবস্থা করত এবং তারাই আত্মসাৎ করত। এরপর আছে পতিত আবাদ। সেদিক দিয়ে কয়েকখানা তৌজিতে অনেক সম্ভাবনা আছে। এ-কাজ রায়দের এস্টেটে অনেক হয়েছে এর আগে। গিরীন্দ্র আচার্য এতে খুব করিত-কর্মা লোক। নদীর ধারের পতিত হলে, নদীর ধার বরাবর বাঁধ টেনে দিয়ে এদেশী মজুর, খেটেখাওয়া লোকদের ডেকে বসাবে চার বছর, পাঁচ বছর পর খাজনা ধার্য হবে, তখন প্রথম দু বছর আধা খাজনা লাগবে, তারপর পুরো খাজনা দেবে। এদিক দিয়েও দশ বছরের মধ্যে আরও সাত-আট হাজার টাকা আয় বাড়বে ষোল মৌজায়। সুতরাং রায়বাড়ীর আয় তখন ষোল মৌজায় দশ হাজারে দাঁড়াবে।
এর মধ্যে সবই কিছু বিনা বাধায় হবে না। বাধা পড়বে। গোপাল সিংহ আছে; এবং প্রায় প্রত্যেক মৌজাতেই দু-একজন করে ছোটখাটো গোপাল আছে; সে সিংহ না হোক, নেকড়ে বা দুষ্ট শেয়ালও হতে পারে। তাছাড়া, আচার্য বললেন—গাঁয়ে নতুন মানুষ দেখলেই দু-চারটে কুকুর লাগে ও তাদের দুমুঠো মুড়ি, দুটো পাঁঠা কাটলে আটটা টেংরী হয়, ছুঁড়ে দিলে তারা পোষ মেনে যাবে। তখন আমরা যার ওপর লেলিয়ে দোব, তাদের ওপরেই লাগবে। তবে গোপালের সঙ্গে হবে। তা হোক। লাঠির পথ গোপালের, আমাদের পথ মামলার চরকীপাকের। ছ’ মাসের মধ্যে বারদশেক সদর হাঁটতে হলেই জিব বেরিয়ে যাবে। সরকারী দপ্তরে ওর নামে দাগও আছে। পাইক হাঙ্গামার সময় সে ছিল, চুয়াড়দের পিছনেও ছিলেন, সেসব থানাতে আছে।
রায় একমনে ভাবছিলেন—ভেবে বলেছিলেন, আমি আর একটা পথের কথা ভাবছি। কিছু টাকা খরচ হবে। মৌজায় মৌজায় এক-একটা দেবস্থল আছে। সেগুলো জমিদারী স্বত্বের অন্তর্গত। সেখানে ঘরটা মেরামত করানো, কিছু সংস্কার; আর ফি গ্রামে সরকারী পুকুর যা আছে, তার মধ্যে ভাল যেটি, সেটিকে ভাল করে কাটিয়ে দেওয়া। এতে লোকে খুশী হবে। আর কীর্তিহাটে একটা বাংলা ইস্কুল। ওটার কথা বলতে গেলে এই সব কাজের মধ্যে মনেই পড়েনি। ওটাকে আমি করে ফেলতে চাই।
—দাঁড়াও বাবা। এই কাজটি হয়ে যাক। মা-লক্ষ্মী আসবার কথা, তিনি আগে আসুন, ঘরে ঢুকুন। তারপর মা-সরস্বতীর পাটন হবে। মনে যখন করেছ, তখন হবে বৈকি। তুমি কীর্তিহাটের রায় এস্টেটের মালিক, তুমি মনে করেছ যখন তখন হতেই হবে। একটা কেন, ইচ্ছে করলে পাঁচটা হতে পারে। সেই তো আমাদের মনের খেদ বাবা বীরেশ্বর। তোমার এমন বিষয়বুদ্ধি। তুমি এমন ইংরিজী বল। এই তোমার রাজপুত্রের মতো চেহারা, তুমি একটা ধাক্কাতে সবকিছু ছেড়ে—।
চুপ করে গেলেন। তারপর কথা খুঁজে নিয়ে বললেন, ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম, জমিদার, লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক, গান-বাজনা, বাঈ—এসব তোমরা না করলে করবে কে? বলতে গেলে তো ওরা তোমাদের দয়াতেই বাঁচে। আর ওসব হল শোভা। নাহলে মানায়ও না। তারপর দুটো-তিনটে বিয়ে এ তো সাধারণ লোকে করে গো। তা ওই যে বউমা গেলেন, আর তুমি সব ছেড়ে বিবাগী হয়ে কলকাতায় এসে সব ছেড়েছুড়ে—। না, না। এ চলবে না বাবা। সোফিয়াবিবি আছে থাকুক। বাগানবাড়ী কর। সেখানে রাখ। আর তুমি বিয়ে কর। এতবড় বংশ, বংশধর চাই। ভাগ্নেতে সব পাবে, এটা—। মানে আমাদেরও ভাল লাগে না।
রায় সজাগ হয়ে উঠলেন। বললেন, হ্যাঁ। এবার ভেবেছি এমনভাবে আর না। হ্যাঁ, কাজকর্ম নিয়েই থাকব। আপনি কাগজপত্র নিয়ে রাজাবাহাদুরের কাছে চলে যান। সব পাকা করে দলিলপত্র শেষ করে ফেলুন।
বলে বাইরে এসে বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলেন।
ইচ্ছে হয়েছিল এক মাসের উপর হয়ে গেল গান-বাজনা করেননি, আজ সোফিকে ডেকে শেষ গান-বাজনা করে ওকে বিদায় দেবেন।
সঙ্গে সঙ্গে ডেকেছিলেন-মহেন্দ্ৰ।
—আজ্ঞে। মহেন্দ্র চব্বিশ ঘণ্টাই হাজির থাকে কয়েক হাতের মধ্যে।
লোক পাঠিয়ে দে সোফির ওখানে। বলবে -আজ একবার আসতেই হবে। মনটা বড় চঞ্চল করে দিয়ে গেল আচার্য। অন্তরে পশুর ক্ষোভ জেগে উঠছে!
লোক গিয়ে ফিরে এসেছিল সোফির সারেঙ্গীদারকে নিয়ে। সে সেলাম বাজিয়ে বলেছিল, বাঈয়ের তবিয়ৎ এখনও পুরা ঠিক হয়নি হুজুর। মাফি মেঙেছে সে।
—কি হচ্ছে তার?
—বহুৎ দুলা আছে হুজুর।
—চিকিৎসা করাচ্ছে?
—হ্যাঁ। ওই ফকরিসাব দাওয়াই দিচ্ছেন, আওর ঝাড়ফুঁক করেন। তাবিজ ভি দিলেন।
—ফকীর? ওই পালাবাবা?
—হাঁ হুজুর।
—সে ওখানে আসে নাকি?
—হাঁ, আসে।
কথাটা শুনে মনে বড় ভাল লেগেছিল বীরেশ্বরের। তারপর এই পাঁচ-ছ দিন পর পর লোক পাঠালেন। সকলে বললে বাঈয়ের সঙ্গে দেখা হয়নি। বারান্দায় ঝুঁকে তার মা বলেছে-তার তবিয়ৎ ঠিক নেই। শেষ দিন মহাবীর সিংও এসে তাই বললে, সঙ্গে সঙ্গে বললে, বাঈসাহেবা গানা-বাজনা করছেন।
কেমন একটা খটকা লেগে গেল। মহাবীর সিংকে জেরা করে জিজ্ঞাসা করতেই সে বলে ফেলেছিল, হুঁয়াকা বাজারমে তো লোক বোল রহা হ্যায়—
—কি? কেয়া বোল রহা হ্যায়? আঁ?
—বোল রহা কি—ওই সাধুবাবা বাঈকে গানা শিখাচ্ছেন। বাঈ তো ভাল আছে। আওর-
—আওর কি? বলো! চুপ কাহে? বলো!
—হুজুর, উঁ লোক বোল রহা হ্যায় কি উ সাধু তো মুসলমান বন গিয়া।
—মুসলমান বন গিয়া?
—হাঁ, হুয়াই খাতা হ্যায়, পিতা হ্যায়
—আরে না। উ লোক খানেপিনে সে কুছ হরজা নেহি হোতা বাবা।
মহাবীর এবার নিজেই বললে—নেহি হুজুর, উ লোক বোলতা কি —সাধু ফকীর ভি নেহি হ্যায়। ছোড় দিয়া। উস্তাদকে মাফিক পুষাক পিহিন তা। আওর বাঈকি নিকা করেগা।—
—বাঈকি নিকা করেগা?
—হ্যাঁ, কোই বোলতা সোফি বাঈকি সাথ, কোই কোই বোলতা, নেহি উনকি মাইকি সাথ। বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন বীরেশ্বর রায়।—এও সম্ভব?
তিনি মহাবীরকে বলেছিলেন, যাও। ম্যানেজারবাবুকে ভেজো।
ঘোষ আসতেই বলেছিলেন, সোফিয়ার বাড়ী একবার যেতে হবে তোমাকে। মহাবীর কি বলছে শুনে নাও। তদন্ত করে এস আসল ব্যাপারটা কি! সঙ্গে লোক নিয়ে যাও।
“ধর্মের মধ্যে অধর্ম লুকিয়ে থাকে, ন্যায়ের মধ্যে অন্যায় আছে, পুণ্যের মধ্যে পাপের বাসা আছে, লক্ষ্মীর ছায়ার আড়ালে আড়ালে অলক্ষ্মী! মানুষের মধ্যে অমানুষ—যার আসল রূপ পশুর। হবে না কেন! মানুষ যে জন্তু।”
সুলতা হেসে বললে-বেশ তো বীরেশ্বর রায়ের কথা বলেছিলে সুরেশ্বর, হঠাৎ দার্শনিকতা শুরু করলে কেন?
সুরেশ্বর বললে—কথাগুলো বীরেশ্বর রায়েরই সুলতা। আমার নয়। তবে ওঁর কথা সত্য। খাঁটি সত্য। তাই তোমার মনে হচ্ছে আমি দার্শনিকতা শুরু করেছি আমার জবানবন্দীর সমর্থনে। তবে আর্টিস্ট আমার কাছে তো বাস্তব জগতে এর চেয়ে বড় সত্য আর নেই। কারণ লাইট আর শেড-এ দুটো পাশাপাশি না থাকলে কোন ছবিই প্রাণ পায় না। ছবি ছবিই থেকে যায়। তাই কথাগুলো মুখস্থ হয়ে আছে। বীরেশ্বর রায় বোধ হয় কথাগুলি সেদিন সেই মুহূর্তেই লিখেছিলেন। নায়েব ম্যানেজার ঘোষকে নিজে দেখে তদন্ত করতে পাঠিয়ে অস্থির হয়ে উঠেছিলেন রাগে এবং আক্রোশে।
“সাধুরা পাথরের দেবতা খাড়া করে মহান্ত হয়ে বসে, তাদের ভোগ রাজভোগ, বিলাস রাজার চেয়েও বেশী। তান্ত্রিকের ভৈরবী থাকে। কুলবধূকে স্বর্গের লোভ দেখিয়ে বের করে নিয়ে যায়। বৈষ্ণবদের সেবাদাসী থাকে। আমার জমিদারী থেকে এদের আমি চাবুক মেরে বের করব। আর, ম্যানেজার ফিরে আসুক, তার কাছে জানি সে কি বলে, তারপর আমি নিজে যাব এবং এ যদি সত্য হয় তবে ওই পাগল পিশাচকে আমি খুন করব। কিছু অবিশ্বাস নেই। এরা তান্ত্রিক, অনেকে বলে মড়ার মাংস খায়। সাধনার জন্যে নরবলি দেয়, বামাচারীরা মেয়ে নিয়ে সাধনা করে। সাধনা না ছাই। কুৎসিত ব্যভিচার। সত্য হলে আমি খুন করব।”
“সে পরিত্রাণ পেয়েছে আমার হাতের নাগালের বাইরে চলে গেছে। কিন্তু এ পাবে না। না না।
নায়েব ঘোষ ফিরে এল। তার গলা পাচ্ছি।”
এরপর সুলতা, বীরেশ্বর রায়ের লেখা এলোমেলো। বোধ হয় রাগে উন্মত্ত হয়ে উঠে- ছিলেন। লিখেছেন—“লোকটা একটা কাউয়ার্ড। কথা বলতে পারছে না, মাথা চুলকোচ্ছে, ভয়ে যেন কেমন হয়ে গেছে। কেবল বলছে তান্ত্রিকদের কাণ্ড। তান্ত্রিকদের কাণ্ড। আমি কিল মারলাম, ধমক দিলাম, আমার হাতের কিলের ঘায়ে তেপয়ার মাথাটা ভেঙে গেল। পিশাচ পশু। অ্যান্ড দ্যাট বিচ। বিশ হাজার টাকা। তারও বেশী। হিসেব নেই। দু বছরে—। তার ছবির সামনে বসে তাকে আমি দেখিয়ে ভালবেসেছি।”
সুরেশ্বর বললে-আমি তার থেকে অনেক কষ্টে সবটা বুঝেছি।
নায়েব এসে বলতে পারেনি; তার সঙ্কোচ হয়েছিল, হয়তো ভয় হয়েছিল, যা দেখেছে তা বলতে।
মাথা চুলকে বলেছিল—আজ্ঞে হুজুর, ওঁরা তান্ত্রিক সিদ্ধপুরুষ, ওঁদের কাণ্ড তো। মানে বোঝা—কি ক’রে বলব—
বীরেশ্বর রায় সামনের তেপায়াটার উপর দুরন্ত ক্রোধে একটা কিল মেরেছিলেন, তেপায়ার টপটা ফেটে গিয়েছিল।
ধমক দিয়ে বলেছিলেন—কি ক’রে বলবে? যেমন ক’রে মানুষ কথা বলে তেমনি ক’রে বলবে। যা দেখেছ তাই বলবে। তোমার কাছে কোন ব্যাখ্যা শুনতে আমি চাইনি!
নায়েব ম্যানেজার ঘোষ কোনরকমে বলেছিল—আজ্ঞে মহাবীর যা শুনে এসেছে—
—হ্যাঁ। কি? তাই সত্যি?
—আজ্ঞে দেখে তো তাই লাগে।
কয়েক মুহূর্ত চুপ করে সামনের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে, বোধ হয় কি করবেন ভেবে নিলেন বীরেশ্বর রায়। তারপর বললেন—হুঁ। যাও তুমি।
আবার কয়েক মুহূর্ত চুপ ক’রে থেকে গম্ভীর উচ্চকণ্ঠে ডাকলেন—মহাবীর! আবদুলকে গাড়ী তৈয়ার করতে বলো। তুমি তৈয়ার থাকো। বলেই ঘরের দিকে ফিরলেন কিন্তু আবার ফিরে এসে বারান্দায় রেলিংয়ে ভর দিয়ে বললেন—সুখদেও পাহলওয়ানকে সাখমে লেনা। হাতিয়ারবন্ধ হোকে যানা। বলেই ভিতরে ঢুকে মহেন্দ্র চাকরকে বললেন—বোতল গ্লাস আন। আর জুতো দে।
তাঁর সেই শখ করে কেনা কালো ঘোড়া দুটোর জুড়িতে উঠতে উঠতে হুকুম করেছিলেন- বহুবাজার। সোফিয়া বাঈয়ের মোকাম। জলদি!
সুরেশ্বর বললে–সেখালে চাকরকে মনিবের মেজাজটা আগে বুঝতে হত। যে বুঝত সেই থেকে যেত হয়তো গোটা জীবন। না-হলে দুদিন পর জবাব হয়ে যেত। কোনরকমে চাকরি টেকলেও একপাশে পড়ে থাকত। আবদুল মহাবীর সুখদেও এরা ছিল বীরেশ্বর রায়ের পেয়ারের লোক। মেজাজ বুঝত এবং সেই মেজাজ যা চাইত তা করতে তারা দ্বিধা করত না। আবদুল সেই তেজী কালো ঘোড়া দুটোর লাগাম একবার টেনে ধরেই ঢিল দিয়ে ইশারা দিয়েছিল—’জোর সে বেটা লোক। এবং সঙ্গে সঙ্গে হাতের চাবুকের দড়িটা শূন্যে শিস্ দিয়ে উঠেছিল হাওয়া কেটে।
তখন কলকাতা এ কলকাতা নয়। চৌরিঙ্গীর ওদিকটায় এবং সাহেবদের এলাকায় রাস্তা পাকা এবং সমতল হলেও দেশী লোকের বসবাসের অঞ্চলে রাস্তা অসমান, খানাখন্দে ভরা-ধুলো ওড়ে। সঙ্কীর্ণ রাস্তা, দুপাশে গলি আর ঘুঁচি। খোলার চালের বস্তি। মাঝে মাঝে পাকা বাড়ী। তাও পুরনো।
সন্ধ্যার মুখ, সঙ্কীর্ণ রাস্তাগুলোতে অন্ধকার জমেছে, পাশের দোকানের বড় কুপীগুলোতে দুটো নলের মুখে দুটো ক’রে ধোঁয়াটে লালচে আলোর শিখা জ্বলছে। ধুলোয় ধোঁয়ায় যেন কুয়াশার মতো জমেছে। কিন্তু মনিবের হুকুমে আবদুলের হাতে কালো জুড়িগাড়ীর চাকা লোহার হালে ঘর্মর শব্দ তুলে প্রচণ্ড জোরে ছুটে চলেছিল। ধর্মতলার পর উত্তরমুখে, পুরানো কসাইটোলা-হালের বেন্টিঙ্ক স্ট্রীট-ধরে লালবাজারে মোড় ফিরে বউবাজার পৌঁছতে ওই কালো জুড়ির দেরী হয় নি। রাস্তার লোকেরা সভয়ে দুপাশে সরে দাঁড়িয়েছিল। সহিস দুটো তফাত-তফাত—হুঁশিয়ার—শব্দ ক’রে ঘোড়ারও আগে আগে ছুটেছিল। আবদুল কোচবক্সে বসে অসতর্ক পথচারীদের দু’চার ঘা চাবুকও মেরেছিল! বউবাজার পৌঁছতে দেরি হয় নি। তবুও বারদুয়েক বীরেশ্বর তাগিদ দিয়েছিলেন —আবদুল!
সোফিয়া বাঈয়ের বাড়িখানা কাঠের রেলিং, কাঠের খুঁটি দেওয়া বারান্দাওয়ালা বাড়ী। একটু আগেই ফিরিঙ্গী কালীর স্থান। তখন সেখানে আরতি হচ্ছে। দেশী ক্রীশ্চান ফিরিঙ্গীরা দাঁড়িয়ে আছে। বেশ একটা ভিড় জমেছে।
গাড়ীখানা থামতেই রায় গাড়ী থেকে লাফ দিয়ে নেমে পড়লেন।
পুরনো আমলের ধাঁচের বাড়ী। মল্লিকবাবুদের ভাড়াখাটানোর বাড়ী। বাড়ীটার উপরে উঠবার সিঁড়ি ঠিক মাঝখানে। রাস্তার উপরে দরজার মুখ থেকে সোজা খাড়া উঠে গেছে উপরে। একেবারে মাথায় খানিকটা প্রশস্ত জায়গা।
রায় মহাবীর সিং এবং সুখদেও পাহলওয়ান’কে দরজায় রেখে বললেন—কোইকো ঘুসনে নেহি দেনা!
উত্তরের অপেক্ষা না করে তিনি উপরে উঠে চলে গেলেন। দু-তিনটে সিঁড়ি উঠেই তিনি থমকে দাঁড়ালেন। মৃদুকণ্ঠের গান ভেসে আসছে। কালোয়াতি উচ্চাঙ্গের গান নয়, সাদা সরল সুরের বাংলা গান। কণ্ঠস্বর চেনা; গাইছে ওই পাগল। সেই মাঠে যেমন শুনেছেন তেমনি না, বোধহয় তার থেকেও প্রাণের রসে মাখামাখি।
চেনা তোকে হল নাক—
জানা তোকে হ’ল না।
বারে বারে দিলি দেখা
ক’রে গেলি ছলনা।
মোহিনী অধরে হাসি—
দেখে কাছে ছুটে আসি
দেখি ভীমা এলোকেশী—
উন্মাদিনী ললনা
চেনা-তোকে হল না—
জা-না-তোকে হল না।
অস্থির পদক্ষেপ তাঁর ধীর হয়ে গেল। ধীর পদক্ষেপে উঠে গেলেন তিনি। উপরে সিঁড়ির মাথায় প্রশস্ত জায়গাটায় ঘরের দরজার মুখে দাঁড়ালেন। যা দেখলেন তাতে তাঁর মুহূর্ত-পূর্বের ধীরতা কোথায় চলে গেল। স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন তিনি।
সে এক অবিশ্বাস্য দৃশ্য।
মহাবীরের শোনা কথা, ম্যানেজার ঘোষের কথা শুনেও এ তিনি কল্পনা করতে পারেননি। একটা পুরু গদীর উপর মখমল বিছিয়ে, পিছন দিকে একটা সাটিনে মোড়া তাকিয়া রেখে, পাগল সামনে একটা নিচু চৌকির উপর পা রেখে বসে আছে আমীর ওমরাহের মত। তার গায়ে গেরুয়া রঙের দামী মলমলের আলখাল্লা, মাথার চুলে তেল পড়েছে, খু তেলের গন্ধ উঠছে। দাড়ি গোঁফ তাও পরিচ্ছন্ন। পাগলের পায়ের উপর হাত রেখে বসে আছে সোফিয়া। সোফিয়ার চিবুকটি বাঁ হাতে তুলে ধরে পাগল একটু ঝুঁকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখছে, চোখের দৃষ্টিতে যেন প্রদীপের শিখার মতো কিছু জ্বলছে। ওই দেখতে দেখতেই গান গাইছে।
পাগলের পিছনে দাঁড়িয়ে একটা বাঁদী। তালপাতার পাখা দিয়ে বাতাস করছে। সোফিয়ার মা পাশে বসে তানপুরার সুর দিচ্ছিল, পাশে একটা তেপায়ার উপর ধুপদানিতে গুগুল লাবান পুড়ছে।
সোফিয়ার বেশভূষা আরও বিস্মিত করেছিল রায়কে। সোফিয়ার পরনে হিন্দুস্থানী হিন্দু মেয়ের পোশাক। গায়ের কাঁচুলির উপর শাড়ী, তাও বাংলাদেশের সাদা জমি লালপেড়ে শাড়ী। চুল তার এলো হয়ে পিঠের উপর পড়ে আছে।
বীরেশ্বর রায়কে দেখেই সোফিয়ার মায়ের মুখ পাংশু বিবর্ণ হয়ে উঠেছিল। হাতের তানপুরায় সুর দেওয়া আঙুলটা আপনিই থেমে গিয়েছিল। সে-ই শুধু তাকে দেখেছিল। সে-ই বসে ছিল দরজার দিকে মুখ করে। সোফিয়া বসেছিল প্রায় পিছন ফিরে পাগলের দিকে তাকিয়ে। বাঁদীরা সম্পূর্ণ পিছন ফিরে ছিল। দেখতে পাওয়া আর একজনের উচিত ছিল, সে পাগলের কিন্তু তার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল সোফিয়ার মুখের দিকে। কোন শব্দ কোন গন্ধ হয়তো বা কোন অনুভব বশেই তার দৃষ্টি সোফিয়ার মুখ থেকে সরিয়ে নেওয়া বা ফেরানো অসম্ভব ছিল। মগ্ন হয়ে গেছে লোকটা। চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে একটা আশ্চর্য মোহে। এমন ক’রে রূপ দেখা বীরেশ্বর কল্পনা করতে পারেন না। শুধু পাগলই বা কেন, সোফিয়াও যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেছে। পিছন দিক থেকে তাকে দেখে মনে হচ্ছে সে নিস্পন্দ স্থির। চোখ তার নিষ্পলক হয়ে গেছে।
সোফির মা তানপুরাটা নামিয়ে রেখে তাড়াতাড়ি উঠে এসে দরজার সামনে প্রায় পথ আটকে দাঁড়াল এবং হাতজোড় করেই বললে—রায়বাবু সাব! এর মধ্যে একটা ইঙ্গিত ছিল। আপনি ফিরে যান। মাফ করুন।
এতক্ষণে চমক ভাঙল বীরেশ্বরের। তিনি এবার তাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ঘরে ঢুকলেন এবং বললেন বহুৎ আচ্ছা!
এবার সোফিয়ার মোহগ্রস্ততা ভাঙল। সে চমকে উঠে মুখ ফেরাল এবং বীরেশ্বর রায়কে সামনে দেখে ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেল। পাগলও এবার চঞ্চল হয়ে দৃষ্টি ফেরালে। তার হাত থেকে মুখ সরিয়ে নিয়েছে সোফিয়া। চোখের সম্মুখ থেকে সোফির মুখ সরে যাওয়াতে সে অধীর চঞ্চল হয়ে সোফি যেদিকে তাকিয়েছে সেদিকে তাকিয়ে রায়বাবুকে দেখে তারই দিকে তাকিয়ে রইল। কিন্তু এতটুকু ভয় ছিল না তার দৃষ্টিতে বা মুখে। তার বদলে ছিল বিস্ময় যেন বীরেশ্বরকে চেনেই না, চিনতে চেষ্টা করছে!
—কিরে, চিনতে পারছিস নে?
তুমি বলতেও ইচ্ছে হয় নি বীরেশ্বরের।
—রায়বাবু? প্রশ্ন করেই কথাটা বললে পাগল!—বীরেশ্বর রায়?
—হ্যাঁ। কী হচ্ছে এসব? সাধনা?
নীরবে ঘাড় নেড়ে সে জানালে-হ্যাঁ। হ্যাঁ। হ্যাঁ।
—কসবীর বাড়ীতে কসবী নিয়ে সাধনা হচ্ছে তোর? পিশাচ ভণ্ড
বাধা দিয়ে সোফির মা বলে উঠল—হজরৎ—উনে হজরৎ হ্যায় হুজুর—
—চোপ! ধমক দিয়ে উঠলেন বীরেশ্বর।
পাগল বললে—সে একবার জলে ভেসে এসেছিল, একবার আমাকে জলে ডুবিয়েছিল, একবার পাহাড় থেকে ফেলে দিয়েছিল। আবার এখানে এনেছে। হেসে বললে-এবার যত্ন কত! দেখ, কেমন আমীর নবাব করে দিয়েছে! দেখ না, মেটেবুরুজে নবাব ওয়াজিদ আলিশা বন্দী হয়ে রয়েছে। আর পথ থেকে ডেকে এনে আমাকে আমীরের মসনদে বসিয়ে ভোলাতে চাচ্ছে। দেখ না।
—জাতটাও দিয়েছিস, মুসলমান হয়েছিস এই কসবীটার জন্যে?
পাগল বার-বার ঘাড় নেড়ে বললে—না-না-না, ওর জাত নেই, ওর জাত নেই।
–ও তোর কে?
পাগল এবার দৃষ্টি বিস্ফারিত করে বললে—জানি না। ও বলছে না।
—তুই বল!
—আমি? ঘাড় নেড়ে পাগল বললে—না —।
—বলতেই হবে তোকে, তোকে আমি বলাব।
বীরেশ্বর রায় অধীর অস্থির। প্রকৃতি যেন পাল্টে গেছে। তিনি তিলে তিলে উত্তপ্ত হয়ে উঠছিলেন। এবার এই মুহূর্তটিতেই বোমবাজির পলতে পুড়ে পুড়ে বিস্ফোরণ হয়ে গেল। তিনি পাগলের ঝাঁকড়া চুল ডান হাতের মুঠোয় ধরে সেখানেই টেনে আছড়ে ফেলে দিলেন।
সোফিয়া চীৎকার করে উঠল।—রায়বাবু! রায়বাবু!
সোফিয়ার মা কেঁদে উঠল।-বাঁদীটা ছুটে গেল বারান্দায়। চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটে গেল—জান বাঁচাও! জান বাঁচাও!
বীরেশ্বর রায় কিছুই গ্রাহ্য করলেন না। তিনি পাগলের বুকে চেপে বসে গলায় হাত দিয়ে বললেন, বল্–বল্ ও তোর কে?
পাগল বিস্ফারিত দৃষ্টিতে বীরেশ্বরের মুখের দিকে তাকিয়েই রইল শুধু। একটা কথাও বললে না। যেন অকস্মাৎ বোবা হয়ে গেছে। কিন্তু তাতে যেন কিছু কথা ছিল।
সুরেশ্বর বললে—বীরেশ্বর রায় লিখেছেন, সুলতা—তাতে যেন জিজ্ঞাসা ছিল। একদিন পর যখন লিখছি তখন আমি শান্ত; মাথার মধ্যে নেশার স্পর্শ নেই। কাল আমার ওই দৃষ্টি দেখে মনে হয়েছিল সে বুঝতেই পারছে না তার এতে অপরাধটা কি হয়েছিল! কিন্তু আজ মনে হচ্ছে, সে কিছু জিজ্ঞাসা করতে চেয়েছিল, চোখে সে জিজ্ঞাসা ফুটে উঠেছিল।
থাক সে কথা। বলব সেটা, বলবার সময় এলে। তবে বীরেশ্বর রায়ের ক্রোধ তাতে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছিল। তিনি এবার—
এবার গলার নলিটা টিপে ধরে নিষ্ঠুর চাপ দিয়ে বলেছিলেন—বল্। বল্—। বল্।
পাগলের মুখখানা অব্যক্ত যন্ত্রণায় বিকৃত এবং নীল হয়ে আসছিল, একটা গোঙানি বেরিয়ে আসছিল-জন্তুর গোঙানির মতো।
রায় নিষ্ঠুরভাবে বলেছিলেন—নিজের গলা নিজে টিপে ধরে বলতিস—ছাড়! ছাড়! বলতে দে! বলতে দে! এমনি ক’রে টিপতিস্? বল্–ছেড়ে দেব! বল্!
সোফিয়ার মাও ছুটে বেরিয়ে গিয়েছিল বারান্দায়। সেও চেঁচাচ্ছিল—জান বাঁচাও! জান বাঁচাও! রাস্তায় গোলমালও কিছু উঠতে শুরু করেছিল। কিন্তু বীরেশ্বর রায় ভ্রুক্ষেপহীন। সোফিয়া পুতুলের মত দাঁড়িয়েছিল। তাদের ঘরে গোলমাল হয়। সে জানে, সে হয়তো তার জীবনে দেখেও থাকবে। কি করবে খুঁজে পাচ্ছিল না। হঠাৎ সে এবার বীরেশ্বরের ডান পায়ের উপর উপুড় হয়ে প’ড়ে পাখানা জড়িয়ে ধরে আর্তকণ্ঠে বলে উঠল—হুজুর, রায় হুজুর, উনি হজরৎ, আমি ওর বাঁদী। হুজুর—
রায় নিষ্ঠুর ক্রোধে তাঁর পা-খানাকে ছুঁড়ে দিলেন, সোফিয়া সেই পা ছোঁড়ার বেগে একটি যন্ত্রণাকাতর শব্দ করে চিৎ হয়ে উল্টে পড়ে গেল। রায় নিষ্ঠুর হেসে বললেন—হ্যাঁ। কসবী যারা তারা সবারই—।
বলতে গিয়েছিলেন-’তারা সবারই বাঁদী’। কিন্তু বলা হল না। তাঁর জুতোর ডগার ঠোক্করে সোফিয়ার উপরের ঠোঁটখানা কেটে দু ফাঁক হয়ে গেছে। রক্ত বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে।
বীরেশ্বর রায়ের হাতের মুঠো আলগা হয়ে গিয়েছিল। চকিতে মনে পড়ে গিয়েছিল দীর্ঘকাল আগের কথা। ছবিটাও ভেসে উঠেছিল তাঁর স্মৃতিতে।
বীরেশ্বর রায় লিখেছেন—মুহূর্তে ঘটনাটা মনে পড়ে গেল। ছবিটা মনে পড়ে গেল। সে ঠিক এমনি ক’রে আমার পায়ের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে বলেছিল—বিশ্বাস কর তুমি। আমাকে এমন ক’রে অপমান কর না। তার থেকে তুমি আমাকে মেরে ফেল। ও গো—
আমি এমনি ক’রেই পা ছুঁড়েছিলাম। সে উল্টে এমনি ভাবেই চিৎ হয়ে পড়ে গিয়েছিল। তারও সেদিন চুল এলো ছিল। পরনে লালপেড়ে শাড়ী ছিল। উল্টে যখন পড়ল তখন তার উপরের ঠোঁটখানা কেটে গেছে। রক্ত বেরিয়ে আসছে।
আমি সেদিন বিচলিত হই নি। তার রক্ত বেরিয়ে আসা দেখেছিলাম বসে বসে। সে হাত দিয়ে ঠোটের রক্ত মুছে একবার হাতখানা চোখের সামনে ধ’রে দেখেছিল। তারপর নীরবে উঠে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গিয়েছিল। আমি মহিন্দরকে ডেকে বলেছিলাম—বোতল গ্লাস আন।
মদ খেতে খেতেই সোফার উপর ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।
সকালে মহিন্দরই আমাকে ডেকে তুলেছিল। ক্রুদ্ধ হয়েই উঠে ব’সে তাকে বলেছিলাম—কি?
মহিন্দির কেঁদে উঠে বলেছিল—রাণীমা—
—কি? রাণীমা কি?
—রাণীমা নাই হুজুর! কাঁসাইয়ের ঘাটে অঙ্গের গয়না খুলে রেখে—
বীরেশ্বর রায়ের সেই সস্মৃতি মনের মধ্যে ভেসে উঠছিল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পাগলের কণ্ঠনালী-ধরা হাতের মুঠে শিথিল হয়ে গিয়েছিল আপনা থেকেই। তিনি পাগলকে ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন।
একি করলেন তিনি। ছিঃ! সোফিয়া কিন্তু তার ঠোঁটের আঘাত ঠিক গ্রাহ্য করেনি। সে তার মত ঠোঁটে হাত দিয়ে দেখেনি কি হয়েছে। কি গড়িয়ে আসছে। সে সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় আঘাত সামলে নিয়ে উঠে বসে তাকিয়েছিল পাগল সন্ন্যাসীর দিকে। এবং কাতর কণ্ঠে ডেকেছিল—হজরত! হজরত! তারপর বীরেশ্বর রায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে তিরস্কার করে বলেছিল—আপনে উনকে খতম কর দিয়া রায়বাবু?
রায় এবার পাগলের দিকে তাকিয়ে দেখেছিলেন। পাগল নিস্পন্দের মত পড়ে আছে। শ্বাসপ্রশ্বাস পড়ছে কিনা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।
সোফিয়া পাগলের উপর ঝুঁকে পড়ে তাঁর মুখের কাছে মুখ এনে আর্তকণ্ঠে ডাকতে লাগল-হজরত। হজরত।
পাগল যেন খাবি খাচ্ছে। সোফিয়া চীৎকার করে ডাকলে-পানি-পানি। আম্মা পানি। সোফিয়ার মা তখনও বাইরে চেঁচাচ্ছিল। মেয়ের ডাকে ঘরে এসে চীৎকার করে উঠল- খতম কর দিয়া?
—পানি। পানি আম্মা। পানি দো!
জলের বদনাটা এগিয়ে দিল সোফিয়ার মা। সোফিয়া পাগলের মুখে চোখে জলের ঝাপটা দিতে দিতে ডাকতে লাগল —হজরত! হজরত! ফকীর সাহেব!
পাগল চোখ মেলেছে। স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে আছে সোফিয়ার মুখের দিকে। সোফিয়া আবার ডাকলে—বাবা! বাবা সাহেব! বাবা!
পাগল এবার সাড়া দিতে চেষ্টা করলে—কিছু বলবার চেষ্টায় ঠোঁট দুটো ফাঁক হল কিন্তু স্বর বের হল না।
সোফিয়া ডাকছেই আর্তস্বরে—বাবা!
আবার ঠোঁট হাঁ হল। আবার! বীরেশ্বর রায় স্থির হয়েই দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর মনে অনুশোচনা ছিল না। উৎকণ্ঠা ছিল। লোকটা কি মরে যাবে? গলার নলীটা কি ভেঙে গেছে?
না। মরবে না। তবে গলার নলীটা জখম হয়েছে। আওয়াজ বের হচ্ছে না।
ওদিকে দরজার মুখ থেকে মহাবীর ডাকছে-হুজুর! হুজুর!
নিশ্চয় লোক জমে গেছে বাঁদীটা এবং সোফিয়ার মায়ের চীৎকারে। সুখদেও পাহলওয়ানের আওয়াজ আসছে। হট্ যাও! নেহি। নেহি! ঘুসনেকা হুকুম নেহি হ্যায়! রায় আর থাকতে চাইলেন না। পাগলটা মরবে না। কষ্ট পাবে। অ ওর প্রাপ্য। ঠিক হয়েছে। তাঁর শাস্তি দেওয়া হয়ে গেছে।
সোফিয়া ওকে ‘বাবা’ বলে ডাকছে! সোফিয়ার ঠোঁট কেটেছে তাঁর জুতোয়। ঠিক হয়েছে। এও সোফিয়ার প্রাপ্য!
তিনি ফিরলেন। দরজার বাইরে সিঁড়ির মাথায় প্রশস্ত জায়গাটায় দাঁড়ালেন। নিচে অনেক লোক দরজার সামনে। তা হোক তিনি ভয় করেন না। ভুল হয়ে গেছে তিনি নিজে হাতিয়ার আনেন নি।
ঠিক সেই মুহূর্তে কর্কশ ভাঙা একটা অস্বাভাবিক আওয়াজে কে চীৎকার করে উঠল- আঁ-! আঁ―! আঁ!
তিনি ফিরে আর একবার তাকালেন। দেখলেন—পাগল চীৎকার করছে—আঁ! আঁ! আঁ! ঠিক যেন একটা জন্তু চীৎকার করছে। ওটা জন্তুই। মানুষ হয়ে জন্মালেও ওটা জন্তু ছাড়া কিছু নয়।
তিনি নেমে এলেন নিচে।
সামনে একটা জনতা জমেছে। তারা একটু দূরে দাঁড়িয়ে সুখদেও আর মহাবীরের দিকে তাকিয়ে আছে। মহাবীরের হাতে তলোয়ার, সুখদেওয়ের হাতে একটা লাঠি। সুখদেও পাহলওয়ানের বিপুল শরীর এবং মহাবীরের হাতের তলোয়ার দেখে তারা এগিয়ে আসতে সাহস করছে না।
বীরেশ্বর নিচে রাস্তায় নেমেই বললেন—যাও, সব চলে যাও। কুছু নেহি হুয়া। যাও—যাও! হিন্দু সন্ন্যাসীটা আওরতের লোভে মুসলমান হতে যাচ্ছে বলে আমি ওকে থোড়া কুছ সাজাই দিয়েছি। ব্যাস। যাও—যাও।
বলতে বলতেই তিনি গিয়ে গাড়ীতে উঠলেন। আবদুল লাগামের টানে জিভের শব্দে ঘোড়া দুটোকে ইসারা দিলে—চল।
ঘোড়া ছুটল লালবাজার স্ট্রীট মুখে।
সুখদেও মহাবীর ছুটল আগে এবং পিছনে তাদের সঙ্গে সহিস দুটো। হট্ যাও-হট্ যাও।
প্রচণ্ড জোরে ছুটেছিল বগিগাড়ীখানা। লোকে তফাত হয়ে পথ দিলে। কিছু দূর এসে সুখদেও ও মহাবীর উঠল গাড়ীর পিছনে আর কোচবক্সে। সহিস দুটো ছুটল সামনে।
পিছনে তখন একটা বচসা লেগে গেছে। হিন্দু এবং মুসলমানেরা পরস্পরের সঙ্গে কথা কাটাকাটি শুরু করে দিয়েছে।
গাড়ীর মধ্যেই তার একটা অনুশোচনাও হয়েছিল। পাগলের জন্য নয়, হয়েছিল সোফিয়ার জন্য। মন বলছিল অন্যায় হয়ে গেল। ওটা অন্যায় হয়ে গেল।
সোফিয়া কসবী বাঈজী। এই তার পেশা। এই তার ধর্ম। এককালে সে মুজরো করে খেতো। শৌখীন ধনীর সঙ্গে অর্থবিনিময়ে রাত্রিযাপন করত। তিনি তাকে অর্থ দিয়ে নিজের সম্পত্তি করে নিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সে তাঁর দেওয়া অর্থের চেয়ে বেশী অর্থ পেলে অবশ্যই তাঁর সঙ্গে ফারখত করে চলে যেতে পারে।
এই পাগলটাকে অর্থের জন্য না হোক তার ওই ভেল্কির জন্য যদি তার আনুগত্য স্বীকার করে, তবে তাতেই বা তাঁর বলবার কি আছে?
হ্যাঁ, কিছু কিছু নারী পাগল আছে যারা এর জন্য খুন-খারাপী করে। তিনি তাঁদের দলের নন। না না। এটা অন্যায় হয়ে গেছে।
দোষ সোফিয়ার নয়। দোষ ওই ভণ্ড পিশাচের। ওদের এমনতর অনেক ভেল্কি আছে যাদু আছে যার বলে মানুষকে বিশেষ ক’রে দুর্বলচিত্ত মানুষকে, যাদের মধ্যে মেয়েরাই বেশী, পোষা জন্তুর মত বশীভূত করে ফেলে।
বাড়ি এসে পৌঁছেই তিনি ওপরে উঠে গিয়েছিলেন। মহিন্দরকে ডেকে হুকুম করেছিলেন —বোতল গ্লাস আন!
মহিন্দর বোতল গ্লাস সাজিয়েই রেখেছিল। ঢেলে দিয়েছিল গ্লাসে। জল মিশিয়ে দিয়েছিল। বীরেশ্বর মদের গ্লাসটা হাতে নিয়ে ঘরময় একপাক ঘুরে গ্লাসটা টেবিলের উপর নামিয়ে দিয়ে বলেছিলেন—ঘোষবাবু ম্যানেজারকে ডাক।
ঘোষ এসে দাঁড়াতেই বীরেশ্বর বললেন—কাল সকালে মহাবীর সুখদেওকে বাদ দিয়ে অন্য দারোয়ান সঙ্গে ক’রে একবার সোফিয়া বাঈজীর বাড়ী যাবেন। সঙ্গে এক হাজার টাকা নিয়ে যাবেন, ওকে দিয়ে আসবেন। বলবেন—ওকে আর আমার দরকার হবে না। বুঝলেন! ঘোষ হুকুম শুনেও গেল না। দাঁড়িয়ে রইল। বীরেশ্বর জিজ্ঞাসা করলেন-কি? ঘোষ বলে—একটা ‘এলিবি’ রাখলে হত না? মহাবীর যা বললে—
—কি? ওরা থানাপুলিশ করবে?
—তা—
—করুক। আপনি যান।
—আমি অবিশ্যি ঘনশ্যাম পরামানিককে পাঠিয়েছি। বউবাজার অঞ্চলেই ও ইঁট পেতে বসে কামানের কাজ করে। বলে দিয়েছি খবরটা জেনে আসতে।
হেসে বীরেশ্বর বলেছিলেন—আচ্ছা।
বীরেশ্বর রায় এরপর লিখতে বসেছিলেন। ওই খাতায় লিখেছেন —সোফিয়ার ওখান থেকে ফিরে এসে লিখে রাখছি যা হয়েছে। ঘটনাটা সমস্ত লিখেছেন—
ঘোষ ‘এলিবি রাখতে বললে। আমার হাসি এল। সামান্য একটা তান্ত্রিক সাধু আর একটা কসবী বাঈজীকে যদি খুন করেই আসতাম, তাতেই বা কি হত? লোকটা অত্যন্ত দুর্বল লোক ভীতু!
জমিদারী করতে গেলে এ হয়। একটা দুটো কেন দু-দশটা খুন হয়ে যায়!
বলরামপুর কাশীজোড়ার জমিদার চৌধুরী বীরপ্রসাদ মেদিনীপুর শহরে সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ চাটুজ্জে-বাড়ীর মেয়ে জবরদস্তি তুলে নিয়ে গিয়েছিল। মেদিনীপুরের লোকেরা একজোট হয়ে মামলা করিয়ে চৌধুরীকে সাজা দিইয়েছিল। তিরিশ ঘা বেত। বেত খেয়েছিল চৌধুরী কিন্তু আঘাত তার লাগেনি। বেত মারবার লোকের সঙ্গে বন্দোবস্ত করেছিল, এমনভাবে বেত মারবি যাতে শব্দ হবে খুব, কিন্তু চৌধুরীর পিঠে পড়বে ফুলের ঘায়ের মত। এক এক বেতে দশ বিঘে লাখরাজ মিলবে। হয়েও ছিল তাই। চৌধুরী বেত খেয়ে অক্ষত দেহে গায়ের পিরহান চড়িয়ে ঘোড়ায় চড়ে চলে গিয়েছিলেন। তিনশো বিঘে লাখরাজের সনদ দিয়ে গিয়েছিলেন লোকটাকে!
এ তো একটা কসবী আর একটা পাগলা বাউণ্ডুলে গাঁজাখোর লম্পট! যাদু আর ভেল্কি দেখিয়ে বেড়ায়! লোকটা না মরলে আমি খুশী হব। আমার সাজা হবে এই ভয়ে নয়। আমি দেখতে চাই এই লোকটার পরিণতি কি হয়।
মরে এবং মরবে সবাই, সে পরিণতি নয়। এই জন্তুটা শেষ পর্যন্ত কি জন্তুতে দাঁড়ায় তাই আমি দেখতে চাই।
জন্তু অবশ্য সবাই। হ্যাঁ—সবাই। রাজা বাদশা, নবাব থেকে ভিখিরী পর্যন্ত। নবাব সিরাজ- উদ্দোলা ফৈজী বাঈজীকে দেওয়াল গেঁথে অন্ধকূপে পুরে মেরেছিল। আরও অনেক কথা শোনা যায়। বড় রাজা বাদশার ইতিহাস সব তাই। সব তাই। তারা প্রকাশ্যে হত্যা করে। বিচারের নাম ক’রে করে। ঔরংজেব বিচার করে ভাইকে কেটেছিল। গুণ্ডাতে চোরাগোপ্তা খুন ক’রে মারে। একটা মহান্ত একটি তের বছরের মেয়েকে রেপ করে মেরে ফেলেছিল বাবার আমলে। রাজা বাদশা নবাব জমিদার চোর গুন্ডা সন্ন্যাসী মহান্ত সব জন্তু, এ ছাড়াও খোঁজ করলে দেখা যাবে সবাই জন্তু। ধার্মিক বিমলাকান্ত কুটিল জন্তু। আমিও জন্তু। হ্যাঁ, আমিও জন্তু। আমার এই খাতাখানা উল্টে উল্টে দেখলাম। দেখলাম যা করেছি তার সবই তো জন্তুর আচরণ। তবে আমি ওদের থেকে কম জন্তু। তা না-হলে আজ ওই সাধুটাকে আর সোফিয়াকে খুন করতে পারতাম আমি। কি হত? টাকার জোর থাকলে হয় না কিছুই। এবং অন্যায় করতাম না। অন্যায়ের সাজাই দিতাম। এরই মধ্যে একটা-আধটা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আসে। রাধাকান্ত দেব আসে। ওরা দুনিয়ার সৃষ্টিতে অর্থহীন ব্যতিক্রম! কারণ ওরা কিছুই করতে পারে না।
খাতা উল্টে দেখছি আর নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করছি—এগুলো কেন লিখে রাখি? কেন?
এসব স্মরণ ক’রে কি ফল? বিচার করে দেখছি কিছু না। আজ থেকে ঠিক করলাম আর লিখব না। এইটেই আমার শেষ স্মরণীয় ঘটনা হয়ে রইল। তলায় লিখে দিচ্ছি—দি এণ্ড!
এর পর সুলতা, সুরেশ্বর বললে—সত্যই বীরেশ্বর রায়ের খাতাটা সাদাই থেকে গেছে। অন্তত আরও শতখানেক পৃষ্ঠা তাতে ছিল। সব সাদা। সব সাদা!
ওদিকে ঘড়িতে ঢঙ ঢঙ ঢঙ শব্দে তিনটে বাজল।
হেসে সুরেশ্বর বললে—সেদিনও, মানে বীরেশ্বর রায়ের ডায়রীটা এই পর্যন্ত প’ড়ে বাকি সাদা পাতাগুলো ওলটাচ্ছি আর ভাবছি—তারপর? তারপর কি হল? মনের মধ্যে অসংখ্য প্রশ্ন আমার। বীরেশ্বর রায়ের জীবনে ভবানী দেবী ফিরে এসেছিলেন। কি ক’রে এলেন? এলেন যদি তবে বীরেশ্বর রায় তাকে নিলেন কি করে?
তাঁর ডায়রীর মধ্যে দেখছি তিনি তাঁর মুখে লাথি মেরেছিলেন। মেরেছিলেন সন্দেহবশে। বিমলাকান্তকে জড়িয়ে সে সন্দেহটা।
ঠিক এমনি সময়ে সুলতা, কীর্তিহাটের বিবিমহলের বদ্ধঘরের স্তব্ধ অন্ধকার আবহাওয়াটা চঞ্চল হয়ে উঠেছিল ঘড়িতে পাঁচটা বাজার শব্দে!
ঢঙ ঢঙ করে পাঁচটা বেজেছিল।
ততক্ষণ পর্যন্ত ওই লেখাটায় একেবারে পরিপূর্ণভাবে মগ্ন হয়ে গিয়েছিলাম, বোধহয় বারেকের জন্যও চোখ তুলিনি। এবার চোখ তুলে দেখলাম, জানালার ফাঁক দিয়ে বাইরের আলো আসছে। এতক্ষণে শব্দও কানে এসে পৌঁছুল। কাঁসাইয়ের ওপারে বনটায় কাকেরা ডাকছে। ওরাই সংখ্যায় বেশী। মধ্যে মধ্যে কোকিল ডেকে উঠছে খুব ঘন বা ক্ষিপ্র কুহু কুহু কুহু কুহু শব্দে।
আমি আলোটা ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিয়ে উঠে এসে জানালা খুলতে যাচ্ছি এমন সময় নীচে থেকে ডাক শুনলাম-রাজাভাই। ভাই রাজা!
ঘুরে এসে রাস্তার ধারের জানালাটা খুললাম। ঘরের কেরোসিনের গ্যাস মেশানো বাতাসে ভারী বুকটা বাইরের ঠাণ্ডা বাতাসে জুড়িয়ে গেল। একেবারে যেন সেকালের ভারী আমল থেকে একালে এলাম।
দেখলাম একখানা টাপর দেওয়া গরুর গাড়ী নামাচ্ছে গাড়োয়ান। গাড়ির টাপরের ভিতর থেকে মুখ বের করে ব্রজেশ্বরদা ডাকছে—রাজাভাই।
জিজ্ঞাসা করলাম—কি? গাড়ী কেন?
গাড়োয়ান গাড়ী থামালে। ব্রজদা গাড়ি থেকে নেমে বললে-পালাচ্ছি ভাই। সূর্য না উঠতেই পালাচ্ছি।
—পালাচ্ছ?
—হ্যাঁ। বাবার বক্তৃতা, বিষয় নিয়ে কূটকচালী ঝগড়া—এসব ভাই সইত। কিন্তু অতুলে- শ্বরের দায়ে যে হাঙ্গামা লাগল রায়বাড়ীতে এ ভাই সইবে না। পালাচ্ছি। আবার যদি বেটারা আজকে আসে আর বাড়ীসুদ্ধ লোককে নিয়ে টানাটানি ক’রে তবে রাজাভাই মরেই যাব।
দেখলাম ওদিক থেকে অর্থাৎ ঠাকুরবাড়ীর দিক থেকে আসছেন মেজঠাকুমা, অর্চনা এবং ব্রজদার বউ।
ব্রজেশ্বর বললে—একটু চা খাওয়াও ভাই। রঘু উঠেছে?
সুরেশ্বর বললে—ব্রজেশ্বরদা সেই দিনই চলে গিয়েছিল সুলতা। চা-টা খেয়ে যাবার সময় বলেছিল—রাজাভাই, খুব সাবধানে থেকো। মেদিনীপুর যা হয়ে উঠেছে, তাতে জান-মান কিছু থাকবে না। আমি খবর সবই রাখি। পলিটিক্সে আমি এখন দস্তুরমত ওয়াকিবহাল আদমী। রাজা, মহারাজকুমারকে খবরের কাগজ পড়ে আমাকে শোনাতে হয়। তাতে এখন প্রজাভাইটি অনায়াসে অ্যাসেম্বলী কাউনসিলে গিয়ে বক্তৃতা করতে পারে। তবে কংগ্রেস-টংগ্রেস নয়। বশম্বদ রাজা-জমিদার পার্টির একজন জোরালো সভ্য হতে পারে। কিন্তু টাকা চাই, নয় তো কংগ্রেসী হতে হবে। বাস্, ও আমি হতে পারব না। জেলকে তবু সইতে পারি, ঠ্যাঙানীকে আমার বড় ভয়। কাল অতুল-খুড়োর যা হাল দেখলাম, দেখেই আমার দেহপিঞ্জর ভেঙে প্রাণবিহঙ্গ পালাবার জন্যে মাথা ঠুকছে। এরপর যে কি হবে তাই ভাবছি। রায়বাড়ীর ছেলে বলে যদি ধরে নিয়ে গিয়ে একটা ঝাঁকি দেয়, তবে গলগল করে সব বলে ফেলব। কাল সারা রাত্রি ঘুমুইনি রাজাভাই। ঘুমটি সবে এসেছিল; বউ অঘোরে ঘুমিয়ে গেছে, একটু একটু নাকও ডাকছে, আমার সবে তন্দ্রা নেমেছে, এমন সময় পাশের ঘরের দরজা খুলল। পদধ্বনি উঠল, সঙ্গে সঙ্গে কাপড়ের একটু খসখস আর ফিসফিস কথা। চমকে উঠে পড়লাম। পুলিশ-টুলিশ এল নাকি? মেজদি অৰ্চনা উঠল কেন? বুঝেছ? তারপরই আর কি, জানালার আড়ালে এসে দাঁড়ালাম। দেখলাম, তোমার বাড়িতে আলো জ্বলছে, জানালা খোলা। এঁরা দেখলাম চলে গেলেন। ছাদের উপর পায়ের শব্দ পেলাম। তারপর টর্চ সঙ্কেত। মোট কথা ভাই, সমস্ত একেবারে রায়বাহাদুরের খাস কাছারী—দেওয়ানী খাস পর্যন্ত যা ঘটেছে সবই দেখেছি। তবে হলটা কি তা ঠিক জানি নে। কিন্তু কিছু যে হয়েছে এবং সেটা যে আমার খুড়োবাহাদুরের সঙ্গে জড়ানো, তাতে আমার সন্দেহ নেই। বুঝলাম তুমিও জড়িয়ে পড়ছ। গাড়ী আমার বলা ছিল। আজই আমি যেতাম। কিন্তু খেয়ে-দেয়ে। সে মতলব বর্জন করে ভোররাত্রে উঠে গাড়ীটাকে ডেকে এনে রওনা দিচ্ছি। অতুলখুড়োর জন্যে আমার আশঙ্কা নেই। ওর বুকে বাঁশ দিয়ে ডললেও ও কথা বলবে না। ফাঁসি ও হাসি মুখেই যেতে পারবে। ভয় আমার ওই অর্চনার জন্যে, তোমার জন্যে, আর অতুল-খুড়োর মা-যশোদা ওই মেজদির জন্যে। তুমি অনিচ্ছে সত্ত্বেও জড়াচ্ছ তা আমি বুঝতে পারছি। ভাল হচ্ছে না। তুমি এক কাজ করো ভাই রাজা, যথাসম্ভব শিগগির ওই অর্চনা আর মেজদিকে নিয়ে এখান থেকে কলকাতায় চলে যাও। এখানে থেকো না।
কথাগুলো ব্রজদা আমাকে একান্তে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলেছিল সুলতা।
আমি স্থিরদৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবছিলাম—এই মিষ্টিমুখ মনোহর রায়- বংশধরটি শেষ পর্যন্ত মেদিনীপুর বা কলকাতার পুলিশ হেড কোয়ার্টারে যেতে পারে কিনা! তাকে বিশ্বাস তো অসম্ভব। কলকাতার বিডন স্ট্রীটের ধারের গলিতে শেফালী বলে বেশ্যা মেয়েটির কাছে যে ব্রজেশ্বর সুরেশ্বর নাম বলে আমাকে বিপদগ্রস্ত করতে দ্বিধা করেনি, একটা দেহ-ব্যবসায়িনীর সঙ্গে প্রতারণা করতে ইতস্তত করে নি, সে কি আর এটা পারবে না?
ব্রজেশ্বরদা চতুর, কিন্তু এত চতুরতা আমি ভাবিনি। সে আমার চাউনি দেখেই আমার মন বুঝেছিল। বলেছিল—তুমি যা ভাবছ রাজাভাই, আমি তা সমঝা হুঁ। নাঃ—সে ভয় করো না। বিভীষণ হবার মত সাধ্যি আমার নেই, তরণীসেনের মৃত্যুবাণ রামকে বলতে পারা সোজা কথা নয়, ব্রাদার! বিশ্বাসটা রেখো। তবে ভয় আমার প্রহারকে। ওইটে সহ্য করতে পারব না বলে পালাচ্ছি। বউকেও বলব না। নিশ্চিন্ত থাক।
কথাটা মেজদি, অৰ্চনা এবং ব্রজেশ্বরের বউ এদের থেকে সরে গিয়ে নির্জনে হচ্ছিল। চায়ের কাপটা ছিল হাতে। সেটা নামিয়ে দিয়ে বললে—কাল রাত্রে শুধু নিজের ভয়ে অস্থির হইনি; সাবাসও দিয়েছি। অতুলখুড়োকে কখনও প্রণাম করিনি আজ পর্যন্ত। সে বিজয়ার দিনও নয়। কাল তাকে প্রণাম করেছি। তোমাদেরও সাবাস দিয়েছি। অর্চনা মেজদির চেয়ে তোমাকেই বেশী দিয়েছি। কারণ তোমার সঙ্গে অতুলের স্নেহ বল, ভালবাসা বল, এসব কিছু নেই; ওদের আছে। ওরা টানে করেছে। তোমার টানটা যদিই থাকে তবে মেজদির টান। আর বংশের জন্য টান। কাল বলছিলে, অতুলের ছবি আঁকবে। তখনই সেটা মালুম হয়েছে আমার।
ব্রজদা কথা কইতে ধরলে আর ছাড়ে না। বলেই যাবে। বলেই যাবে। সম্ভবত ওইটেই তার মুলধন। ওদিকে সূর্য তখন উঠে পড়েছে; কাঁসাইয়ের বনের গাছগুলোর মাথায় রোদ চিক-চিক করছে। রায়বাড়ীর শ্যাওলা-ধরা চিলে-কোঠার আলসেতেও রোদ এসে পড়েছে। গাড়োয়ানটা নিচে থেকে হাঁকলে, বাবুমশায়। আর দেরী করলি পর বাস ধরা যাবেক নাই।
রাস্তা কম নয়; পাঁশকুড়ো গিয়ে ট্রেন, রাস্তা প্রায় বারো ক্রোশ, চব্বিশ মাইল। এখান থেকে মাইল পাঁচেক গিয়ে বাস। সেই বাস ধরতে হবে।
ব্রজদা ঘড়িটা দেখে বললে—তাই তো রে বাপধন! মনে করিয়েছিস ভাল। এই এলাম রে বাপ্। তাহলে চলি রাজাভাই। বলে সে হাঁকতে হাঁকতেই চলতে শুরু করলে, কই মেজদি? তোমাদের হয়েছে তো? কি সব খাওয়াবে, তা হল? না হয়েছে তো থাক। চোখের জল ফেলাটা সেরে ফেল।
আমিও তার সঙ্গে সঙ্গে এসেছিলাম নিচে পর্যন্ত। হঠাৎ কি মনে হল বললাম, টাকা-কড়ি আছে তো? মানে দরকার নেই তো?
ব্রজেশ্বর বলেছিল—ও কথা আর জিজ্ঞাসা কর কেন রাজা। খোদ ইংলন্ডেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করে দেখ—সেও বলবে আছে। তবে তোমার কাছে টাকা আজ কিছুতেই নেব না, রাজা- ভাই। তুমি ভাববে মুখ বন্ধ করে থাকব, তার দাম চাচ্ছি। অতুল যা দেখিয়ে গেল, রাজাভাই, তারপর সবে একটা রাত কেটেছে। আজ আর টাকা নেব না। দিলেও না।
ব্রজদার বউ গাড়িতে উঠল। ব্রজদা উঠতে যাচ্ছিল, অর্চনা বললে—দাঁড়াও, বউয়ের পা মুছে নিই, নিতে হয়।
মেজদি চোখের জল মুছছিলেন, বলেছিলেন—আর দু-চারটে দিন থেকে গেলেই তো পারতিস ব্রজ। এসে বললি, সাত দিন থাকবি। তা তিনটে দিন পার না হতেই চলছিস।
—তোমার মনে নেই ঠাকুমা, দাদু বলতেন, ভাগ্যে মিউটিনি হয়েছিল তাই কীর্তিহাটে রায়েরা পাকাপোক্তভাবে এখানে এসে শেকড় গেড়েছিল। নাহলে বীরেশ্বর রায় কলকাতা শহর, সোফি বাঈজী-টাইজী ছেড়ে এখানে এসে আর বাস করতেন না। তিনি তো প্রতিজ্ঞা করেই ছেড়েছিলেন কীর্তিহাট। আমি বীরেশ্বর রায়কে সবসে বড়া রায় বলে মানি। কিন্তু অধম বংশধর। টাকা নেই। ঠাকুমা সত্যি বলছি;—আজ মেদিনীপুরে তিন-তিনটে ম্যাজিস্ট্রেট মরল, পল্টন এনে ইংলন্ডেশ্বর জেলাটা চষছে, আর অতুল-খুড়ো কিনা রায়বাড়ীতে তেরঙ্গা ঝাণ্ডা ওড়ালে। এই অবস্থায় টাকা থাকলে আমি আজই ইংলন্ডের টিকিট কিনে জাহাজে চড়তাম। দুটো টিকিটের টাকা থাকলে বউ নিয়েই যেতাম। না থাকলে, একটা টিকিটের টাকা থাকলেও বউকে রায়বাড়ীতে সাবিত্রী ব্রত করতে বলে রেখে পালাতাম।
বলে সে গাড়ীতে চড়ে বসল।
কথাটা গল্প নয়, কথাটা সত্য সুলতা। বীরেশ্বর রায় মিউটিনির ধাক্কায় কীর্তিহাটে এসে বাস করেছিলেন। প্রথমে ইচ্ছে ছিল মিউটিনির হাঙ্গামা মিটলেই চলে যাবেন। যাই হোক, এসপার ওসপার একটা হয়ে যাক। ইংরেজ থাকলে যেমন ছিলেন, তেমনি থাকবেন। ইংরেজ যদি হারেই তবে কলকাতা তো থাকবে, উঠিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না। তবে গোলা মেরে ভেঙে-চুরে দিয়ে যাবে। তা যাক, সারিয়ে-টারিয়ে নিয়ে বাস করবেন। বাংলাদেশের নবাব যিনিই হোন, সে মুরশিদাবাদের নবাবই হোন, আর মেটেবুরুজে বন্দী অযোধ্যার নবাব ওয়াজিদ আলি শা-ই হোন, তাঁকে নজরানা আর কুর্নিশ দিয়ে বাস করবেন।
সুলতা প্রশ্ন করলে-পেলে কোত্থেকে? বীরেশ্বর রায় তো আর কিছু লেখেন নি বললে!
সুরেশ্বর বললে, পেয়েছি চিঠি থেকে। জমিদারী সেরেস্তা একটি আশ্চর্য যাদুঘর সুলতা। কাগজপত্রের যাদুঘর। এখানে এক টুকরো কাগজ নষ্ট করতে মানা। সে কালে জমিদারেরা বলতেন—লক্ষ্মী চঞ্চলা। এই চঞ্চলাটিকে সোনার শেকল পরিয়ে বাঁধা যায় না, ওঁকে বাঁধতে হয় গণেশ আর সরস্বতীর পাকানো হিসেবের দড়ির তৈরী জালে। কাগজের উপর হিসেব- নিকেশ আর প্রমাণপত্রের ফাঁদ ছিঁড়তে উনি পারেন না। জমিদারী সেরেস্তার পাটোয়ারীরা বলে, দু বিঘে চার বিঘে জমি তারা কলমের খোঁচায় গেঁথে রামের হাত থেকে বিনা ফৌজদারীতে শ্যামকে দিতে পারে। পুকুর চুরি কথাটা চলিত, শোনাও যায়, শুনে হাসিও পায়, কিন্তু সত্যি সত্যিই পুকুর চুরি হয় জমিদারী সেরেস্তায়। আগে বলেছি তোমাকে, ঠাকুরের গহনা চুরি ঢাকবার জন্যে মেজঠাকুরদা এক গাদা জমাখরচের খাতা গায়েব করেছিলেন। সোমেশ্বর রায়ের জীবনের ঘটনাগুলো চিঠিপত্র থেকে পেয়েছিলাম। এক এক আমলের চিঠিপত্র বড় বড় পুলিন্দায় বেঁধে শক্ত কাপড়ের গায়ে কালি দিয়ে লিখে তাড়াবন্দী সাজানো ছিল। কোনটায় লেখা—মামলা সেরেস্তার চিঠি কোনটার লেখা গোমস্তা দিগরের চিঠি, কোনটায় লেখা সরকার বাহাদুরের চিঠি। কোনটায় লেখা নোটিশ-পত্রাদি।
এ আমলের ফাইল আর কি! কোন-কোনটায় লেখা খাস চিঠিপত্র।
হেসে সুরেশ্বর বললে—কাগজের ফাঁস সত্যিই মা লক্ষ্মী কাটতে পারেন না। কিন্তু মা লক্ষ্মীর সহায় ওখানে মা ষষ্ঠী। লক্ষ্মীপেঁচার ঠোঁটের ধারে যে জাল কাটে না, তা ষষ্ঠীমায়ের অনায়াসে দাঁত নখে কেটে ফাঁক করে দেয়। ফাঁক দিয়ে মা লক্ষ্মী বাহনের পাখায় ভর দিয়ে পাল দরুনে বংশধরদের আড়াল রেখে পালান। জালটা পড়ে থাকে ধুলোর জঞ্জালে। ষষ্ঠী—মায়ের দেওয়া গণ্ডা গণ্ডা বাছাধনদের তখন দুধ গরম হয় ওই কাগজের জালের আগুনে।
সেদিন আর আমার অস্বস্তির শেষ ছিল না। যার জন্যে এত ব্যগ্রতার সঙ্গে রায়বংশের কথা জানতে চেয়েছিলাম, তার প্রথমটা হল সেটেলমেন্টের তাগিদ; আমার জ্ঞাতিদের প্রতারণা থেকে আত্মরক্ষার প্রমাণ ছিল কাগজে এবং বংশের ইতিহাসের মধ্যে। তারপর যে তাগিদটা এল, সেটা তোমার এবং আমার মধ্যে যে সম্পর্ক তার ভিতটা নড়ে গেল ওই কাগজ থেকেই। ঠাকুরদাস পাল! তাকে পিদ্রু গোয়ান খুন করেছিল।
ঠাকুরদাসের প্রথম পক্ষের স্ত্রী-পুত্র ঘরে আগুন লেগে পুড়ে মরেছিল। ঘর জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন বীরেশ্বর রায় জমিদারী শাসন করবার জন্য।
তারপর রায়বাহাদুরের আমলে রায়বাহাদুরের সঙ্গে ঠাকুরদাস কি বচসা করে কোন্ একটা গুপ্ত কথা বলে দেবে বলে শাসিয়েছিল। ঘটনাটার অব্যবহিত পরেই পিদ্রুর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছিল, পিদ্রুর এক বোনের ব্যাপার নিয়ে। ঝগড়া করতে করতে বাইরে গিয়েছিল দুজনে। এবং নদীর ঘাটে পিদ্রু ঠাকুরদাস পালের বুকে ছোরা মেরেছিল।
রায়বাহাদুর ঠাকুরদাস পালের নামে পাশের গ্রামে ইস্কুল করে দিয়েছেন, আবার পিদ্রুকে মামলায় বাঁচাবার জন্যেও চার অঙ্কের টাকা খরচ করেছেন। পিদ্রুর মেয়ে হিলডাকে জমি দিয়েছেন, গোয়ানপাড়ার ‘মণ্ডলানি’ করে দিয়েছেন।
সমস্ত ঘটনাগুলো লোকেরা জানে, কিন্তু কেন তা জানে না। আমি ব্রজদার কাছে বীরেশ্বর রায়ের এবং রায়বাহাদুরের ডায়রী পেয়ে সাগ্রহে প্রথম থেকে পড়তে শুরু করে হঠাৎ মাঝখানে ডায়রীটা শেষ হয়ে যাওয়ার নিদারুণ অস্বস্তিতে পড়েছিলাম। মনের মধ্যে তখন অহরহ দাঁড়িয়ে আছেন ভবানী দেবী। ওই অয়েল পেন্টিংএর ভবানী দেবী। রাজরাণীর মতো সর্বাঙ্গে অলঙ্কার-মণি-মাণিক্যের ছটা। সিংহাসনের মত আসনখানার হাতল ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। বোধহয় ষোড়শী। মুখে তাঁর আশ্চর্য লাবণ্য। চোখে তেমনি একটি দীপ্তি! আগের দিন রাত্রে ওই খাস কাছারী ঘরে টর্চের আলোয় কয়েক মিনিট দেখেছি মাত্র। বীরেশ্বর রায়ের ডায়রী পড়ে মনে মনে ভবানী দেবীর যে ছবি এঁকেছিলাম, তার থেকে এ ছবি অনেক উজ্জ্বল।
বীরেশ্বর রায় বিয়ের সময়ের স্মরণীয় কথার মধ্যে ভবানী দেবীর রূপের কথা লেখেন নি তেমনি করে যেমন করে গুণের কথা লিখেছেন। এমন কি ছটা আঙুলের কথাও লেখেন নি। লিখেছিলেন, শ্যামবর্ণা মেয়ে। কাজেই মনের তুলিতে উজ্জ্বল রূপের রঙ আপনা থেকেই বাদ পড়েছিল।
রায়বংশের ইতিহাস আমি ছবিতে এঁকেছি। ভবানী দেবীর ছবি রয়েছে, ওই দেখ, ওই দেখ। ওই গান গাইছেন তানপুরা হাতে। বীরেশ্বর রায়ের মামাতো ভাইয়ের আসরে, তাঁর পূর্বরাগের ছবি। আর ওই বর ও বধূর ছবি। ওতে তাঁর সে অসামান্যতা নেই। সায়েব পেন্টারের আঁকা সেই আশ্চর্য ছবিখানা নকল করবার চেষ্টা করেও আমি পারি নি। লজ্জিত হয়েছি। কিন্তু ওই ছবিখানি ছাড়া অন্য ছবিও এর মধ্যে দিতে মন সরে নি। কিন্তু আমার হাতের রায়বাড়ীর ইতিহাসের ছবির মধ্যে সে ছবিও দিতে পারি নি। ওই এক পাশে ছবিখানি আলাদা করে টাঙিয়ে রেখেছি। সব শেষে একটু দূরে; কাপড় দিয়ে ঢাকা আছে।
সুরেশ্বর উঠে গেল এবং লম্বা বারান্দা ঘেরা ঘরখানার একপ্রান্তে, প্রস্থের দিকে দেওয়ালে টাঙানো একখানা মাত্র ছবির ঢাকাটা টেনে খুলে দিলে। মাথায় একটা আড়াইশো পাওয়ারের বাল্ব জ্বলছিল; সেই আলোয় ছবিখানা ঝলমল করে উঠল।
সত্যই সে শ্যামবর্ণা ষোড়শী মেয়েটি অপরূপা এবং মহিমাময়ী।
সুলতাও দেখতে দেখতে আপনার অজ্ঞাতেই বোধ হয় পায়ে পায়ে উঠে কাছে গেল। অয়েল পেন্টিং কিছুটা দুর থেকে দেখতে হয়, একথা তার অজানা নয়, ওই রূপের মহিমা সুষমা তাকে টেনে নিয়ে গেল।
সুরেশ্বর বললে—সেদিন, আগের দিন রাত্রে দেখেছি। পরের দিন সকালে ডায়রীটা যখন মাঝখানে থেমে গেল, তখন থেকে ওই ছবির ভবানী দেবী আমার মন জুড়ে এমন করে দাঁড়ালেন, যে আর আমার মনে কিছুই রইল না। অর্চনার মুখে এই মুখের আশ্চর্য আদল রয়েছে, কিন্তু এ মহিমা কোথায় পাবে সে? তবুও অৰ্চনা গায়ের রঙে গৌরী।
সুলতা বললে—হ্যাঁ, রূপের মধ্যে এ মহিমা যদি শিল্পীর তুলির জাদুতে হয়ে থাকে, তবে বলব সে আশ্চর্য শিল্পী। আর এ মহিমা যদি সত্যই ওঁর রূপের মধ্যে থাকে, তবে তিনি মহিমাময়ী!
ছবিখানার উপর ঢাকাটা আবার টেনে দিলে সুরেশ্বর। বললে—ওটা ঢাকা থাক। নাহলে আমার জবানবন্দী শেষ হবে না, আমি বলতে বলতে থেমে যাব, তুমি ছবি দেখতে গিয়ে অন্যমনস্ক হবে। চল, বসি গিয়ে।
আসনে এসে বসে সুরেশ্বর বললে —সেদিন তোমাকেও ভুলে গেলাম সুলতা। মনে মনে প্রায় অধীর অস্থির হয়ে উঠেছি। এই ভবানী দেবী সম্পর্কে বীরেশ্বর রায় তাঁর স্মরণীয় ঘটনার খাতার মধ্যে বার বার অবিশ্বাসের ইঙ্গিত করেছেন। বার বার ইঙ্গিতে বিমলাকান্তকে জড়িয়ে নির্মম আক্রোশ প্রকাশ করেছেন। বিমলাকান্ত সন্তান কমলাকান্তকে নিয়ে এত বড় বিষয়ের ছ আনা অংশ ছেড়ে দিয়ে চলে গেছেন। চলে গেছেনই বা বলব কেন, সত্য বলতে পালিয়েছেন! বীরেশ্বর রায়ের লেখার মধ্যে এই নারী সম্পর্কে অগাধ আসক্তির পরিচয় পেয়েছি; তিনি এ সম্পর্কে সত্য কথা লিখতে গিয়েও লিখতে পারেন নি। যে আমলে সম্পত্তিবান কুলের অধিকারীরা দুটো-চারটে বিয়ে করে, সেই আমলে বীরেশ্বর ভবানী দেবী জলে ঝাঁপ দেবার পরও বিয়ে করেন নি।
বংশের কলঙ্কের ভয়ের কথার উল্লেখ আছে। লিখছেন—সে লিখতে পারলাম না। এক জায়গায় আছে—
I shall die-with this truth buried in my breast.
ডায়রীর শেষ ঘটনা তান্ত্রিককে গলা টিপে ধরার সময় সোফিয়া বাঈজী তাঁর পা চেপে ধরেছিল, তিনি পা ছুঁড়ে তাকে ফেলে দিতে গিয়েছিলেন, তাঁর জুতোর ঠোক্করে সোফিয়ার ঠোঁট কেটেছিল। তিনি এইখানে লিখেছেন, তাঁর মনে পড়ে গিয়েছিল যে, ভবানী দেবীও ঠিক এইভাবে কাতর মিনতিতে তাঁর পা চেপে ধরেছিল বিবিমহলে, তিনি সেদিনও এমনি করে পা ছুঁড়েছিলেন, যার ফলে এমনিভাবেই ভবানী দেবীর উপরের ঠোঁটটা কেটে গিয়েছিল। ঘটনাটা মনে পড়ার জন্যই তাঁর হাতের মুঠো আলগা হয়ে গিয়ে ছাড়া পেয়েছিল তান্ত্রিক।
ডায়রী এখানেই শেষ করেছেন দারুণ আক্ষেপে।
মানুষ জন্তু। জন্তুর আবার স্মরণীয় ঘটনা কি? The end লিখে দাগ টেনেছেন, বাকী পাতাগুলো সাদা!
মন অধীর হয়ে বলছিল, এ যদি সত্য হয়, তবে আজই ভূমিকম্প হয়ে গোটা রায়বাড়ী ভেঙে-চুরে যাক, আর রায়বাড়ীর সকলেই তার মধ্যে চাপা পড়ে যাক।
বাইরে যারা যেখানে আছে রায়বংশের, শেষ হয়ে যাক শেষ হয়ে যাক। এই মহিমাতেও যদি কলুষের কালি পড়ে থাকে—
সুলতা বাধা দিয়ে বললে—কিন্তু তুমি তো জানতে সুরেশ্বর যে ভবানী দেবী আবার ফিরে এসেছিলেন। তাঁর একটি কন্যা হয়েছিল। তাই কি প্রমাণ করে না যে, বীরেশ্বর রায় এক্সেসিভ ড্রিঙ্কিং-এর ফলে ক্রেজি হয়ে গিয়েছিলেন। ডিজিড মাইন্ড হয়ে গিয়েছিলেন।
সুরেশ্বর বললে—বিবাহের পর থেকে মদ তিনি ছেড়েছিলেন।
—কিন্তু শেষের দিকে আবার ধরেছিলেন।
—ধরেছিলেন এটা সত্য। সেটা ওই সন্দেহ জাগবার পর।
—কিন্তু তাতে কি? নিলেন কেন আবার? তুমিও ক্রেজি। এক্সকিউজ মি!
সুরেশ্বর বললে—আমি ক্রেজি তা আমি জানি। যখন প্রথম দাড়ি-গোঁফ রাখি আমার মায়ের আপত্তি সত্ত্বেও তখন আয়নার মধ্যে নিজের ছবি দেখে বার বার নিজেকে জিজ্ঞাসা করেছি, কেন? দাড়ি রাখলাম কেন? তবু কামাই নি। এবং সম্ভবতঃ পুরনো সম্পত্তিশালী বংশের ওটা একটা পরিণতি। এক্ষেত্রে কিন্তু তা নয়, সুলতা। আমার কথা শেষ করতে দাও। বলতে দাও, তাহলে বুঝবে।
ব্রজদা যাবার সময় বলে গেলেন—বীরেশ্বর রায় মিউটিনির সময় পালিয়ে এসেছিলেন কীর্তিহাটে। সে কীর্তিহাট থেকে বউ নিয়ে পালাচ্ছে অতুলেশ্বর তেরঙ্গা ঝাণ্ডা তুলে পুলিশ হাঙ্গামা রায়বাড়িতে ঢুকিয়ে দিয়ে গেল বলে। সেই কথাটা সত্যি বলে, কাগজের মুল্যের কথা উঠল। তা থেকে তুমি প্রশ্ন তুলে গোল বাধাচ্ছ।
বীরেশ্বর রায়ের সন্দেহ কি করে নিরসন হয়েছিল, সেইটে জানবার আগ্রহে তখন আমি অধীর।
সীতাকে রামের চেয়ে কেউ বেশী চিনত না, বেশী জানত না। সেই রাম রাবণকে বধ করে সীতাকে উদ্ধার করেও অগ্নিপরীক্ষা চেয়েছিলেন। এবং সবার থেকে তাঁর উদ্বেগই ছিল বেশী। তোমাকে অতিরঞ্জন করছি না, আমার উদ্বেগ সেদিন সেই উদ্বেগ! সীতার পাতাল প্রবেশের মত ভবানী দেবীর এমনই ধরনের মৃত্যু হলে আমি তখন লব-কুশের মতো বুক চাপড়ে কেঁদে ধন্য হতে চাই। তোমার ঠোঁটে সূক্ষ্ম হাসি ফুটেছে সুলতা। বুঝতে পারছি সীতার উপমা দেওয়াতে তুমি আমাকে সেন্টিমেন্টাল ভাবছ। হ্যাঁ, সেন্টিমেন্টাল মুডে বাস্তব জীবনকে বিচার করতে গেলে ভুল হয়। দড়ি দেখে সাপ ভেবে অকারণ হৈ-চৈ করে লোক জড়ো করে। না, আমি তা করি নি।
ভবানী দেবী তখন আমার কাছে সত্যই রায়বংশের সীতার মত হয়ে উঠেছেন। বীরেশ্বর রায় নিজেও তাই ভেবেছেন। আমি জানি, অগ্নিপরীক্ষা হয়ে গেছে। আমি সেই কাহিনীর জন্য অস্থির, অধীর!
ব্রজদা চলে গেল। মেজঠাকুমা এবং অর্চনা দাঁড়িয়ে রইল। গেল না। আমি তখন রায়- বাহাদুরের ডায়রীটা খুলবার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছি। যদি ওর মধ্যে থাকে। থাকা সম্ভব। সম্ভব কেন, নিশ্চয় আছে! কিন্তু ওদের জন্য খুলতে পারছি না। চলে যেতে বলতেও পারছি না। বার বার তাকাচ্ছি অর্চনার মুখের দিকে। ঠিক ভবানী দেবী!
মনে আছে, অর্চনার সঙ্গে প্রায় প্রতিবার চোখাচোখি হয়েছিল। তাতে অৰ্চনা লজ্জায় লাল হয়ে উঠে বলেছিল-আমার উপর খুব রেগেছ, না?
আমি বলেছিলাম–না।
—তবে? তবে এমন করে তাকাচ্ছ কেন?
—বীরেশ্বর রায়ের স্ত্রী ভবানী দেবীর অয়েল পেন্টিং ওই খাস কাছারীতে টাঙানো আছে। দেখেছিস কখনও?
হ্যাঁ, জানিয়ে ঘাড় নাড়লে সে। এবং আরও লজ্জা পেলে।
মেজঠাকুমা বললেন—হ্যাঁ, ও তারই মত দেখতে! তবে তিনি ছিলেন শ্যামবর্ণ, আর ও ফরসা।
আমি সুযোগ পেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম- তুমি জান ঠাকুমা, তিনি স্বামীর উপর অভিমান করে কাঁসাইয়ে ডুবে মরব বলে ঝাঁপ খেয়েছিলেন। তারপর কি করে বাঁচলেন, ফিরলেন?
—ওরে বাপরে! সে কথা সবাই জানে। ওঁর জন্ম হল দেবী অংশে। যখন বিয়ে হয়, তখন আমার দাদাশ্বশুরকে প্রতিজ্ঞা করতে হয়েছিল যে মদ তিনি ছোঁবেন না। প্রথম ক বছর মদ ছোঁন নি, স্ত্রী নিয়ে একেবারে পাগল। একবার নাকি কত্তার বাঁ হাতটার বাঈ ফুলে খুব বেদনা হয়েছিল। রাজার ছেলে, রাজামানুষ, সঙ্গে সঙ্গে বদ্যি, ডাক্তার। তাঁরা আর কিছুতেই কমাতে পারে না। কেন কমে না? তখন প্রকাশ হল, প্রকাশ করে দিলে ভবানী দেবী যে তাঁর মাথার চাপে হয়েছে। সারা রাত ওঁর হাতের ওপর মাথা রেখে শুতে হয় ওঁকে। বালিশে মাথা দিতে দেন না। তারপর ছেলে হয়ে মারা গেল! ওই তাতেই আবার বেগড়ালেন উনি। মদ শুরু করলেন। তা সে তো দেবী অংশে জন্ম ওঁর, ওঁর সহ্য হল না। উনি কাঁসাইয়ে ঝাঁপ দিলেন। কিন্তু মরেন নি, ভেসে গেলেন। সাগর দ্বীপের কাছে। সেখানে এক কালীস্থান আছে, সেইখানে সন্ন্যাসিনী হয়ে সত্যিকার তপস্যা করেছিলেন। তারপর কত বছর পর যখন স্বামী মরো-মরো তখন শিয়রে এসে বসেন। কোন আশা ছিল না বাঁচবার। তা ওই সতীর পুণ্যের জোরে বেঁচে উঠলেন। ভাল হলে ভাগ্নে মানে আমার শ্বশুর রায়বাহাদুরকে পুষ্যি নিয়ে সম্পত্তি দিয়ে স্বামী-স্ত্রী চলে গেলেন কাশী।
মনটা আমার শান্ত খানিকটা হয়েছিল, কিন্তু পূর্ণতৃপ্তির স্বস্তি পায়নি। আমার মন চাইছিল পূর্ণ বিবরণ! আমি চুপ করেই থেকেছিলাম।
মেজঠাকুমার মন ভবানী দেবীকে নিয়ে উতলা ছিল না, তাঁর মন অতুলেশ্বরের জন্য ব্যাকুল ছিল, তিনি আমার নীরবতার সুযোগে নিজের কথা পেড়েছিলেন।
—সুরেশ্বর! তাহ’লে—
—কি ঠাকুমা?
—অতুলের জন্যে কিছু ব্যবস্থা করবি নে ভাই? আর তো কেউ কিচ্ছু করলে না। কথাটা মনে হল। হ্যাঁ, কিছু করা প্রয়োজন! বললাম- হ্যাঁ ঠাকুমা, করব বইকি! আমাদের বংশে ও একটি আশ্চর্য ছেলে! একটু হেসে বলেছিলাম-আমি এগিয়ে গিয়েও পারি নি ঠাকুমা।
—না-রে! তুই পিছিয়ে ভালই করেছিস। তাহলে বংশটার আর কিছু থাকত না। তোকে আশ্রয় করেই বিষয়, দেবসেবা, রায়বংশের নাম আজ বেঁচে আছে। তা ছাড়া ছবি এঁকে নাম করেছিস তুই।
আমি কথা না বাড়িয়ে বললাম- তুমি যাও ঠাকুমা, এখনও তো তোমার ঠাকুরবাড়ীর ডিউটি হয় নি। যাও তুমি, আমি আজই নায়েবকে পাঠাচ্ছি, এই সকালেই পাঠাচ্ছি। থানায় যাক। কি বলে দেখুক। তারপর মেদিনীপুর সদরে পাঠাব। উকীলদের সঙ্গে পরামর্শ করে তাঁরা যা বলবেন—তাই করা যাবে!
—আর একটা কথা বলব।
—বল।
—এই মেয়েটার একটা গতি করে দে।
অর্চনাকে দেখালেন ঠাকুমা। অর্চনা একটু চমকে উঠল। ভুরু উঁচু করে বললে—আমার পিছনে কেন লাগলে ঠাকুমা? না। ও সব ভাবনা ভাবতে হবে না, সুরোদা। ও সব করলে আমি একদিন বাড়ী থেকে চলেই যাব। আমাকে খুঁজে পাবে না!
এবার আমি ঠাকুমা দুজনে চমকালাম। ঠাকুমা কেন চমকালেন, তা তিনি জানেন, আমি চমকালাম এই জন্যে যে, অর্চনা তা হলে অতুলেশ্বরের সঙ্গে, এই দলের সঙ্গে এমন করে জড়িয়েছে যে ছাড়াবার উপায় নেই?
সে হন হন করে চলে গেল। মেজঠাকুমাকে বললাম—ওকে রাজী কারও ঠাকুমা, আমি ওর বিয়ে দিয়ে দেব। কথা দিলাম। তবে ভাল করে দেখ, এর সঙ্গে ও কতটা জড়িয়েছে।
ঠাকুমা বিবর্ণ মুখে বললেন—ওরে কলঙ্ক যে আমার হবে। অতুল আমার একটু ন্যাওটা, এ মেয়েটাও খানিকটা বটে। দুজনে যা শলা-পরামর্শ, গুজ-গুজ, ফিস ফাস করে তা আমার ঘরে বসেই করে। লোকে দোষ দিলে তো অন্যায় হবে না সুরো! আমি কি করি বল তো?
কথা কটি বলে, অর্চনাকে ডাকতে ডাকতেই তিনি নেমে গেলেন।—অর্চি, ওরে!
আমি রঘুকে ডাকলাম- রঘু, চা আর কিছু খাবার দে। গতরাত্রি থেকে ভাল করে খাওয়া হয়নি। শরীরটা রাত্রিজাগরণে ঝিম-ঝিম করছিল। নির্জনে এবার আমি রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায়ের খাতাখানা খুললাম। চমৎকার খাতা। কালো চামড়ায় বাঁধানো পুট, কাপড় সাঁটা শক্ত মলাটের খাতা; ফুলস্ক্যাপ সাইজ।
উল্টে দেখলাম—গোটা গোটা অক্ষরে প্রথম পৃষ্ঠাতেই লেখা : জীবনী ও দিনলিপি।
শ্রীরত্নেশ্বর রায়। নিবাস কীর্তিহাট। বঙ্গদেশস্থ জিলা মেদিনীপুর।
“মদীয় মৃত্যুর সময় সজ্ঞান থাকিলে আমি এই দিনলিপি মদীয় চিতায় নিক্ষেপ করিয়া ভস্ম করিতে নির্দেশ দিব। জ্ঞান না থাকিলে ইহা লিখিতেছি যে, একান্তভাবে বিষয়-সম্পত্তির গণ্ডগোল হইলে দিনলিপি পড়িতে, দেখিতে পারেন। তাহাতে অনেক সংশয় মিটিবেক। কিন্তু বংশের ইতিহাস যাহা দিনলিপির অপর পৃষ্ঠায় লেখা থাকিল, তাহা পাঠ করিবেক না। করিলে তাহার উপর আমার অভিশাপ বর্ষিত হইবেক। এবং পরলোকে আমার আত্মা অশান্তির অনলে দগ্ধ হইয়া যাইবেক। সম্ভবতঃ রায়বংশের পূর্বপুরুষেরা নরকস্থ হইবেন।”
আমিও মুহূর্তের জন্য চমকে উঠেছিলাম সুলতা। বিংশ শতাব্দীর বিদ্রোহী বাংলাদেশের ছেলে আমি, আমিও চমকে উঠেছিলাম। এরপরও খুলব? কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভবানী দেবী মনের মধ্যে ভেসে উঠে বলেছিলেন—খোল! তারপর মনে এসেছিলে তুমি। একটা নাম মনে পড়েছিল, ঠাকুরদাস পাল।
মনে মনে বলেছিলাম—’ক্ষমা কর আমাকে। আমাকে জানতেই হবে। মানতে পারলাম না তোমার মানা।’ তারপর উল্টেছিলাম সে পাতাটা। পরের পাতা থেকে শুরু।
ওঁ কালী।
“অদ্য ১২৬৬ সাল, ইংরাজী ১৮৬০ খৃষ্টাব্দ, শকাব্দ ১৭৮১, শুভ দোল পূর্ণিমা তিথি, তারিখ ২০শে ফাল্গুন; সন্ধ্যার পর ভগবানের কৃপা প্রার্থনা করিয়া দৈনন্দিন বৃত্তান্ত অর্থাৎ ঘটনাদি কার্যাদি যাহা মদীয় জীবনে এবং পরিবারস্থ মনুষ্যগণের জীবনে ঘটিতেছে এবং গ্রামে, সমাজে যাহা যাহা বিশেষ ঘটনাবলী সঙ্ঘটিত হইতেছে, তাহা সমুদয় প্রকাশ করিতে সঙ্কল্প করিয়া লিখিতে আরম্ভ করিলাম। রায়বংশের কুলদেবতা জগজ্জননী শ্রীশ্রীশ্রীকালী কীর্তিশ্বরী ও পিতামহ সোমেশ্বর রায় মহাশয় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কল্যাণময় সৌভাগ্যশিলারূপী শ্রীশ্রী জনার্দন দেব এবং কীর্তিহাটের ওপারস্থ সিদ্ধপীঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবী আমার সহায় হোন। নারায়ণী বাগাদিনী দেবী সরস্বতী আমার লেখনীকে সংশয়-মুক্ত করুন।
প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যাহা লিখিব, তাহা সত্য লিখিব। কোনপ্রকার মিথ্যা লিখিয়া সত্য যাহা তাহাকে আচ্ছাদিত করিব না।
তৎসঙ্গে ইহাও লিখিতেছি, ভগবান এবং সকল দেব-দেবীর নিকট মনে মনে ঐকান্তিক ব্যগ্রতা ও লক্ষ লক্ষ প্রণতি নিবেদন-পূর্বক অনুমতি ভিক্ষা করিতেছি অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি যে, রায়বংশে যদি প্রকাশের অযোগ্য কোন কলঙ্ক ঘটে বা পূর্বকালে ঘটিয়া থাকে, তাহা অপ্রকাশ রাখিয়া যাইব। যথা পিতৃপিতামহ কলঙ্ক, মাতৃ-মাতামহী, পিতামহী সম্পর্কিত কুৎসা কলঙ্ক কন্যা-কলঙ্ক। এই ত্রিবিধ কলঙ্ক বা পাপ ইত্যাদি উচ্চারণে যেমন মহাপাপ অর্শায়, লেখাতে তেমনি অর্শিয়া থাকে। সে পাপ যিনি সঙ্ঘটন করিয়াছেন, তাঁহার বিচার করিবেন সর্বনিয়ন্তা যিনি, তিনি।
আজ দোল পুর্ণিমার শুভ পুণ্য দিনে আমি কমলাকান্ত ভট্টাচার্য নাম উপাধির পরিবর্তে রত্নেশ্বর রায় নাম ধারণপূর্বক কীর্তিহাটের রায়বংশের একমাত্র উত্তরাধিকারী হইলাম। মহামান্য পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর রায় মহাশয় আমাকে যথাবিধি যজ্ঞ করণাদি করিয়া পুত্র বলিয়া গ্রহণ করিলেন। অহো! অদৃষ্টের কি চক্রান্ত! অথচ আমি সত্য সত্যই পিতা-মাতার কাছে ফিরিলাম! পোষ্যপুত্র হিসাবে ফিরিলাম।
এতদিন যাঁহাকে পিতা বলিয়াছি, তাঁহাকে আজ পিসামহাশয় বলিয়া জানিলাম। ক্রিয়াদির সময় তিনি ক্রন্দন করিতেছিলেন। আমিও ক্রন্দন করিলাম। শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর রায় এ অঞ্চলে প্রস্তর-হৃদয় মনুষ্য বলিয়া কথিত; এ অঞ্চলের মনুষ্যেরা তাহার ভয়ে ভীত! তিনিও ক্রন্দন করিলেন।
আমি প্রজ্বলিত হোম-অগ্নির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতঃ ভাবিতেছিলাম, আমার অদৃষ্টে এ কি ঘটিল! ইহার উপমা বা তুলনা তো খুঁজিয়া পাইতেছি না।
পুরাণে কথিত আছে, দেব বলরাম মাতা দেবকীর অষ্টম গর্ভে আগমন করিলে দেবগণ, ভগবান কৃষ্ণ দেবকীর অষ্টম গর্ভে আসিবেন বলিয়া সৃষ্টিকর্তা পিতামহ ব্রহ্মার নিকট বার্তা নিবেদন করিলে, ব্রহ্মা দেবকী গর্ভস্থ ভ্রূণবীজকে বৃন্দাবনস্থ বসুদেব-পত্নী রোহিণী দেবীর গর্ভে সঞ্চারিত করিয়াছিলেন। দেব বলরাম দেবকীর পুত্র হইয়াও রোহিণীর পুত্র বলিয়া জগতে খ্যাত হইয়াছিলেন।
মদীয় ভাগ্য, অদৃষ্ট আরও বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং জটিল। আমি রায়বংশের পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াও দৌহিত্র বলিয়া পরিচিত। আমার জন্মদাতা এবং জন্মদাত্রী যিনি তাঁহারাই এত কাল পর আমাকে যজ্ঞ করিয়া পোষ্যপুত্র হিসাবে গ্রহণ করিলেন।
এতকাল পর জ্ঞাত হইলাম, আমি ভবানী দেবীর গর্ভজাত সন্তান। আমার জন্মদাতা পিতা শ্রীবীরেশ্বর রায়।
অথচ এতকাল আমি শ্রীবিমলাকান্তের ও বিমলা দেবীর পুত্র বলিয়া পরিচিত হইয়া আসিয়াছি। অথচ এই সত্য আজ লোকসমক্ষে প্রকাশ করিবার উপায় নাই। তাহাতে আমার এক ঊর্ধ্বতন পুরুষ লোক-নিন্দায় এবং সমাজ-নির্দেশে পরলোকেও অনন্ত নরকগামী হইবেন। সংসারে মনুষ্যগণ পাপ করিয়া থাকে এবং পরলোকে তাহার ফলভোগ অবশ্যই করে। কিন্তু লোকসমাজে তাহা যখন প্রচারিত হইয়া মুখে মুখে ঘোষিত হয়, সমাজকর্তাগণ যখন তাহাকে এই গুপ্ত কর্মের জন্য অভিশাপ দেন, তখন তাঁহার যে পুণ্যটুকুও থাকে, তাহাও অগ্নিমুখে তৃণসম ভস্মীভূত হইয়া থাকে। যাঁহার কথা গোপন করিতে হইল, তিনি সাধারণ মনুষ্যগণ বা চলিত সমাজ-বিধানে বিচারিত হইবার মনুষ্য নন। তিনি মহাসাধক। সারাজীবন কঠিন এবং কঠোর সাধনা করিয়া বজ্রাঘাতে তালবৃক্ষের মত আহত হইয়াও বিনাশপ্রাপ্ত হন নাই। বার বার মরিতে মরিতে বাঁচিয়াছেন। এবং শেষ পর্যন্ত শান্তিতে দেহত্যাগ করিয়াছেন বটে, তবে পূর্ণসিদ্ধি লাভ করিতে পারেন নাই। নিজে বলিয়াছেন, তাঁহাকে জন্মান্তর ধারণ করিতে হইবে সিদ্ধির জন্য।
এই মহাসাধক ছাড়াও আরও এক পূর্বপুরুষ তাঁহার সঙ্গেই মহাপাপ করিয়াছেন। সে পাপ তাঁহাকে দেবতাই ছলনা করিয়া করাইয়াছেন বলিয়া মদীয় দৃঢ় বিশ্বাস হইতেছে।
অতএব এই সত্য প্রকাশ করিতে বিরত থাকিলাম। তবে এই সত্য প্রকাশ করিলাম যে, আমি বীরেশ্বর রায় এবং শ্রীমতী ভবানী দেবীর সন্তান হইয়াও শ্রীবিমলাকান্ত এবং বিমলা দেবীর সন্তান বলিয়া পরিচিত ছিলাম, আবার আজ অদৃষ্ট চক্রান্তে আশ্চর্য বিধানে পোষ্যপুত্র হইয়া পিতা-মাতার ক্রোড়ে এবং রায়বংশের সম্পত্তিতে আবার ফিরিয়া আসিলাম। অদৃষ্টের চক্রান্ত। সাধনায় ভ্রষ্ট হওয়ার কর্মফল বহন না করিয়া মানবের উপায় নাই।
ওই মুখবন্ধের পাতাখানা পড়ে আমার মাথার ভিতরটা ঝিমঝিম করে উঠল। রত্নেশ্বর রায় পোষ্যপুত্র হয়েও পোষ্যপুত্র নন। তিনি বীরেশ্বর রায় এবং ভবানী দেবীর সন্তান হয়েও শৈশব থেকে যৌবনকাল পর্যন্ত সে-পরিচয়ে পরিচিত ছিলেন না। বিমলা দেবী এবং বিমলাকান্তের সন্তান বলে পরিচিত ছিলেন। আবার পোষ্যপুত্র হয়ে ফিরে এসেছেন। কারণ প্রকাশের উপায় নেই। রত্নেশ্বর রায় লিখেছেন, তাতে ঊর্ধ্বতন পুরুষের মহাপাপ প্রকাশ হয়ে পড়বে। প্রকাশ হলে ঊর্ধ্বতন চতুর্দশ পুরুষ নরকস্থ হবেন।
কি সে পাপ?
রায়বাহাদুরের পঁয়তাল্লিশ বছরের জীবনের দৈনন্দিন ঘটনায় দিনলিপি চৌদ্দখানা বাঁধানো খাতায় লেখা আছে। সেগুলো আমার সামনে থাকবন্দী সাজানো ছিল। তখনকার দিনে একালের মত তৈরী ডায়রীর চল হয়নি। ভাল কাগজ কিনে দপ্তরীকে দিয়ে বাঁধিয়ে ছাপাখানায় পুটের চামড়ায় রত্নেশ্বর রায়, সাকিম কীর্তিহাট, লিখিয়ে নেওয়া হত।
সেগুলো আর পড়তে সাহস হয়নি। যেন পঙ্গু হয়ে গেছি মনে হয়েছিল। অথচ আমার ধারণা ছিল স্বর্গ-নরক, পাপপুণ্য ঈশ্বর এসব আমি কিছুই মানিনে। এসব কুসংস্কার, অতীত- কালের বিজ্ঞানবোধহীন মানুষের মনের তৈরী।
অন্যদিকে আমার এতকাল ধরে শোনা কথার রঙে আর কাগজপত্রের তথ্যের রঙে আঁকা কালো-সাদা রঙে আঁকা পুরুষানুক্রমিক রায়দের মিছিলের ছবিটার উপর কে যেন জলে-চোবানো তুলি চালিয়ে ঘষে সব ঝাপসা করে একাকার করে দিলে। শুধু কয়েকটা কালো রেখাই রইল, কিন্তু কালচে হয়ে দুর্বোধ্য হয়ে গেল।
বাঘে যখন সজারুকে আক্রমণ করে তখন সজারু তার কাঁটাগুলো ফুলিয়ে খাড়া করে বসে থাকে, নড়ে না। বাঘ স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে, কখনও থাবা মারতে যায় কিন্তু গুটিয়ে নেয়। সেও জানে—ওই কাঁটাগুলো বিঁধে যাবে, গিলতে গেলে মরতে হবে, তবুও সে নড়ে না। আমি ঠিক তেমনি করেই তাকিয়েছিলাম ওই খাতাগুলোর দিকে।
মনে প্রশ্ন হচ্ছিল হাজার রকম। পাপ? কি পাপ? মানুষ খুন? নরহত্যা? ঘরে আগুন জ্বালানো? ব্যভিচার? চুরি?
এগুলোর সবই রায়েরা করেছে। তা ডায়রীতে গোপন করলেও, জমা-খরচের খাতায় কোন-না-কোন রকমে প্রকাশ হয়ে পড়েছে। জমিদারবংশে জমা-খরচের অঙ্কগুলো শুধু অঙ্ক নয়, ওগুলো লক্ষ্মীকে বাঁধার শেকল। ওখানে তারা জমা বা খরচের অঙ্কপাতে কড়াতেও ফাঁক রাখেনি।
হঠাৎ মনে হল, দরকার নেই আমার এত বিবরণে। আমি ভবানী দেবীর সম্পর্কে যে কথা শুনেছি, তাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। রায়বংশের মায়ের ধারায় কোন বিষ নেই, এই যথেষ্ট। রায়বংশের পুরুষদের ইতিহাসে কুড়ারাম রায় থেকে উনিশশো বিশ-পঁচিশ সালের একজন শ্রেষ্ঠ ইন্টেলেকচুয়াল আমার বাবা পর্যন্ত, এখানে ধনেশ্বরকাকার সেই দৈত্যাকার পুত্রটি পর্যন্ত চরমতম অপরাধ করেছেন, তার মাশুলও দিয়েছেন। এদিকে রত্নেশ্বর রায়, অতুলেশ্বরের পুণ্যের পরিচয়ও রয়েছে। এ-সবই জানি, সহ্য হয়েছে। এর উপরে ঊর্ধ্বতন পুরুষে আরও যদি কোন মহানরকের পাপ করে থাকেন, থেকেছেন। সে জেনে আমার দরকারই বা কি?
আমি টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরির বুদ্ধিবাদী, আমি নিজে আজও এমন কিছু করিনি, যার জন্যে লজ্জাবোধ হতে পারে, মাথা হেঁট হতে পারে, সুতরাং আমি পবিত্র।
মনে আছে সুলতা, পবিত্র কথাটা মনে আসায় আমি হেসেছিলাম। ‘পবিত্র’ কথাটার মানে কি? বড়জোর clean—পরিচ্ছন্নই হতে পারে মানুষ। হ্যাঁ, আমি পরিচ্ছন্ন মানুষ। এক স্টেটসম্যানের চিঠিখানা। না—তাতেই বা আমার লজ্জার কি আছে। ওতেও কোন অপরিচ্ছন্নতা নেই। ওখানে আমি সোজা —স্ট্রেট। যা দেখেছি, দেখে যা মনে হয়েছে, তাই লিখেছি। গান্ধীজী বার বার সত্যাগ্রহ থেকে পিছিয়ে আন্দোলন বন্ধ করেছেন। Himalayan blunder স্বীকার করেছেন। গান্ধীজীর শ্রেষ্ঠ মহত্ত্ব এবং মনের পরিচ্ছন্নতা সেখানেই।
আর আমি মদ্যপান করি। হ্যাঁ করি। কিন্তু আমি জানি-এদেশের মত দেশেও আজ কেউ বলবে না যে, মদ্য পান করা অপরাধ। এ অপরাধে অভিযুক্ত করতে পারেন গান্ধীজী, রবীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্রের মত জনকতক ব্যক্তি। সেখানেই মাথা হেঁট করব। আর কোথাও নয়।
সুতরাং আমি টেনে নিয়েছিলাম ১৮৮০ সালের ডায়রীখানা। ১৮৮০ সালের জমা-খরচের খাতায় ঠাকুরদাস পালের হত্যাকারী পিদ্রু গোয়ানের মামলায় তাকে বাঁচাতে চার অঙ্কের একটা খরচ দেখেছিলাম। ঘটনাটা ওই সালেই ঘটেছে।
পাতার পর পাতা উল্টে গেলাম। একশো কুড়ি পাতায় তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের ডায়রী। এক-এক পৃষ্ঠায় তিনদিন-চারদিনের ঘটনা। আট লাইন দশ লাইনে শেষ। শুধু এক-একটা দিনের ঘটনা পৃষ্ঠাব্যাপী। দু’পৃষ্ঠা খুব কম।
প্রথম পৃষ্ঠাব্যাপী ঘটনা যেটা পেয়েছিলাম, সেটা পড়ে কৌতুক বোধ করেছিলাম। সেদিন তমলুকের এস-ডি-ও, আর সদর থেকে ডি-এম, এস-পি এসেছিলেন স্কুলের প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশনে। স্কুল তার দশ বছর আগে হয়েছে। স্কুলের বাড়ির মাথায় খোদাই করে লেখা আছে—বীরেশ্বর হাই ইংলিশ স্কুল, কীর্তিহাট। ১৮৭০ সাল। তার নীচে লেখা—রত্নেশ্বর রায় দ্বারা প্রতিষ্ঠিত।
একপৃষ্ঠা জুড়ে সেদিনের বিবরণ দিয়েছেন। শেষে, লিখেছিলেন, আজকের দিনটি একটি সত্যকারের শুভ দিবস। বিশিষ্ট রাজপ্রতিনিধিবর্গের সহিত বাক্যালাপে ও দেশসংক্রান্ত নানাবিধ আলাপ-আলোচনায় অতিবাহিত হইল। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট বাহাদুর আমাদের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া উৎসাহিত করিলেন। বলিলেন, সদাশয় গভর্নমেন্ট গুণী-দানশীল জমিদারগণের সর্বদাই সংবাদ রাখিয়া থাকেন। তাঁহার পূর্ববর্তী ম্যাজিস্ট্রেটসাহেব আমার সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন। তিনিও আজ স্বচক্ষে তাহা পরিদর্শন করিয়া উপলব্ধি করিলেন। এবং অবশ্যই তিনি এ সম্পর্কে লাটসাহেবের দপ্তরে জানাইবেন। আমি ভাবিতেছি, এখানকার ক্ষুদ্র দাতব্য চিকিৎসালয়টি বড় করিব। এবং মাতা ভবানী দেবীর নামে একটি নিম্ন-প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করিব।
কিন্তু সে থাক। সেদিন আমি সবটা পড়তেও পারিনি। মন ছুটছিল। ছুটছিল ওই দিনের ডায়রীর সন্ধানে।
পেলাম। জানুয়ারীর ১লা—১৬ই পৌষ, ১২৮৬ সাল থেকে অক্টোবর পার হয়ে নভেম্বরের ৪ তারিখে, ২০শে কার্তিকের ডায়রীতে পেলাম যা খুঁজছিলাম। প্রথম ছত্রেই লেখা।
“কি একটা ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা ঘটিয়া গেল। বুঝিতে পারিতেছি না কি ঘটিল। এমন যে কখনও ঘটিবে, ইহা তো জীবনে কোনদিন ভাবি নাই। ঠাকুরদাস—আমি বাল্যকালে তাহাকে দাদা বলিয়াছি। তাহার কাধে চড়িয়াছি। মনে পড়ে, পিসেমশায় বিমলাকান্ত ভট্টাচার্যের সঙ্গে কীর্তিহাট হইতে চলিয়া গিয়া প্রথম উঠিয়াছিলাম শ্যামনগর। পিসেমশায়কে তখন বাবা বলিতাম। কীর্তিহাটের উত্তরাধিকারী আমি জন্মাবধি সেই বিশাল প্রাসাদে কাটাইয়া ওই ক্ষুদ্র বাটীখানিতে আসিয়া কাঁদিতে লাগিয়াছিলাম। আমার ছোট পনি ঘোড়াটির জন্য যখন ক্রন্দন করিতেছিলাম, তখন ঠাকুরদাস, তখন সে চৌদ্দ-পনের বৎসর বয়স্ক সবল চাষীর পুত্র, সে আমাকে তাহার কাঁধে চড়াইয়া বলিয়াছিল, দেখ, আমি তোমার টাট্টু ঘোড়া অপেক্ষা অধিক জোরে দৌড়িতে পারি। আমার কান্না থামিয়া মুখে হাসি ফুটিয়াছিল। ঘটনাটা একটুকরো ছবির মত বেশ মনে আছে আমার। তাহার পর কলিকাতায় যখন কিছুদিন ছিলাম, তখন সে মধ্যে মধ্যে আসিত। যখনই আসিত, আমার জন্য কিছু না কিছু লইয়া আসিত। খেজুর গুড়, মর্তমান কদলী আনিয়া সে আমার হাতেই দিত। একবার একটা হরিণের বাচ্চা আনিয়া আমাকে দিয়া বলিয়াছিল, দাদা, তোমার জন্যে আনিয়াছি। সে আমাকে দাদা বলিত। আমি তাহাকে দাদা বলিতাম। হরিণটা বাঁচে নাই। যেদিন মরে, সেদিন খুব কাঁদিয়াছিলাম। তাহার পর কাশী যখন গেলাম, তখন আর দীর্ঘদিন দেখা হয় নাই। আমরাও আসি নাই। তাহারও যাইবার শক্তি ছিল না। একাদশ বৎসর পর আমি সতের বৎসরের হইয়া দেশে আসিলাম। তখন আমাকে দেখিয়া তাহার সে কি বিস্ময়! আশ্চর্য হইয়া বলিয়াছিল, এ যে রাজপুত্র হইয়া উঠিয়াছ দাদাঠাকুর। ছেলেবেলায় মনে হইত, তুমি তোমার বাবার মতো দেখিতে, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের ঘরের গুরুপুত্র গুরুপুত্র চেহারা হইবে তোমার বাবার মতো। কিন্তু এখন দেখিতেছি, তুমি দাদাঠাকুর, অনেকটা মামার মতো, রায় হুজুরের মতো গো। চোখের চাউনি অবিকল। নাকের ডগাটাও নাকি তেমনি ফুলিয়া উঠে। কপালে তেমনি তিন-চারিটা রেখা দেখা দেয়। সব মনে পড়িতেছে। তাহার পর নীলকর রবিনসন সাহেবদের সঙ্গে কলহে-বিবাদে, সরকার জমিদারের সঙ্গে বিবাদে সেই ছিল আমার দক্ষিণহস্ত। শেষ আমার পিতা যখন শ্যামনগর পুড়াইয়া দেন, তখন তাহার স্ত্রী-পুত্র পুড়িয়া মরিল। আমি আবার রায়বাড়ীর মালিক হইয়া তাহার বিবাহ দিয়াছি। সে ইদানীং আমাকে তেমন করিয়া ঘনিষ্ঠভাবে পাইত না বলিয়া অভিমান করিলেও, তাহা অপেক্ষা আপনার লোক আর কে আছে?
সেই ঠাকুরদাসদাদা আজ খুন হইয়া গেল!
হইল বলিতে গেলে তাহার পুত্রের অপরাধে। আমার পুত্র দেবেশ্বরের অপরাধে। পিদ্রুর ভগ্নী ভায়োলেটকে লইয়া। লিখিতে আমার লেখনী অবশ অক্ষম হইয়া আসিতেছে। এবং ভীত হইতেছি। মনে হইতেছে বংশাশ্রিত সেই অপরাধের অভিশাপ পারদের মত অঙ্গে ফুটিয়া উঠিয়াছে। দেবেশ্বর আমার পুত্র। সে আমার ভয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু ঠাকুরদাস আমাকে গ্রাহ্য করিল না। ঠাকুরদাস তাহার অধিকারের সীমা অতিক্রম করিয়া আমার মুখের উপর বলিল—। আমি আতঙ্কিত হইলাম, একথা সে জানিল কি করিয়া? একথা জানিতেন পাঁচজন—পিতৃদেব, মাতাঠাকুরাণী, মাতুল ও পিসেমহাশয়, আর জানিতেন পূজ্যপাদ রামব্রহ্ম ন্যায়রত্ন। গিরীন্দ্র আচার্য জানিলেও জানিতে পারেন। কিন্তু ঠাকুরদাস জানিল কোন সুত্রে? সে আমাকে ভয় দেখাইল—সে প্রকাশ করিয়া দিবে। আমি গর্জন করিয়া উঠিলাম, তবু সে ভীত হইল না। পিদ্রু তাহাকে ধমক দিল। ভায়োলেটের ভাই হিসাবে সে নালিশ করিয়াছিল আমার কাছে। তাহার উপর সে আমার প্রিয়পাত্র, দেহরক্ষী। সেও ধমক দিল। ঠাকুরদাস তাহাকে বলিল, তুইও ধমক দিস যে। বেটা নিজের বোনের দোষ পরের খাড়ে চাপাইতেছিস? পিভ্রূ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। ঠাকুরদাসও রুখিয়া উঠিল। আমি বাধা দিলাম, না—। ঠাকুরদাস উদ্ধতভাবে বলিল, আর তবে বাহিরে আয়। দেখি তুই কেমন গোয়ান আর আমি কেমন সদগোপের পুত্। আয় বাহিরে আয়। বলিয়া সে-ই আগে বাহিরে গিয়া তাহাকে আহ্বান করিল। যাইবার সময় পিদ্রু আমার দিকে তাকাইয়াছিল। আমি কিছু ইশারা করিয়াছিলাম? না, মনে পড়িতেছে না। তবে মনে মনে চাহিয়াছিলাম। পিদ্রু তাহা বুঝিয়াছিল। সে ব্যাঘ্রবৎ লম্ফ দিয়া বাহিরে পড়িল, তাহার পর আয়-আয় বলিয়া আগাইয়া গেল। চক্ষের অন্তরালে চলিয়া গেল, আমি দাঁড়াইয়া রহিলাম, ক্রোধে অধীর হইয়া ভাবিতেছিলাম, পিদ্রু যদি হারিয়া যায়, তবে ঠাকুরদাস হয়তো উচ্চকণ্ঠে রায়বংশের সেই কথা চীৎকার করিয়া বলিয়া দিবে। কি করিব? এমন সময় পিদ্রু ছোরা হাতে লইয়া আসিয়া আমার সম্মুখে দাঁড়াইল, বলিল, .. উস্কো জান হাম লে লিয়া হুজুর।
আমি বজ্রাহত হইয়া গেলাম।
লোকজনে এতক্ষণে আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। পিদ্রু বলিল—ঠিক হ্যায়, পাকড়াও হামে। হামার বহিনের বেইজ্জতির হামি বলা লে লিয়া। মেইরী হামাকে জরুর মাপ করবেন। হাঁ, জরুর মাপ মিলেগা আমার।
আমি বোধ হয় টলিতেছিলাম। কে যেন আমাকে ধরিয়া ফেলিল। মাথার মুখে জল দিয়া শোয়াইয়া দিল। বাকি দিনটা শুধু শুইয়াই ছিলাম। ঠাকুরদাসের জন্য কাঁদিয়াছি। ঠাকুরদাসদাদা নাই। কিন্তু দোষ আমার নহে, তাহার।
সে আমাকে ওই কথা প্রকাশ করিয়া দিব বলিয়া ভয় দেখাইল। সম্ভবতঃ আমার পুত্র এ কথা বলিলে—ঠিক এমনি পরিণতি ঘটিয়া যাইত। ঠাকুরদাস তাহার বাল্যের দাবীতে আজিকার সম্পর্কটা ভুলিয়া গিয়াছিল।
খাতাখানা বন্ধ করে রেখে দিলাম সুলতা। মাথার ভিতরটা কেমন ঝিমঝিম্ করছিল। এরপর? এরপর কি করে কি বলে তোমার সামনে গিয়ে দাঁড়াব?
গোপন ক’রে রাখব তোমার কাছে? না, সে ইচ্ছে আমার হয়নি। অনেক ভেবে ঠিক ক’রেছিলাম তোমার কাছে ফিরব তোমাকে ডেকে ডায়রীর পাতা পড়াব। সমস্ত বলব। ব’লে তোমাকে জিজ্ঞাসা করব—এরপর কি তুমি এই ঘটনা সম্পূর্ণ মন থেকে মুছে ফেলে আমার জীবনের সঙ্গে জীবন জড়াতে পারবে?
সারাটা দিন উদ্ভ্রান্তের মত ওই ঘরটার মধ্যেই বসে ছিলাম। স্থির কিছু করতে পারিনি। যেটা স্থির করি সেটা আবার অস্থির হয়ে যায়।
যে প্রশ্ন নিজে নিজেই করেছিলাম—সুলতা কি সব শুনে এই ঘটনার প্রতিক্রিয়া মন থেকে মুছে ফেলতে পারবে? উত্তর নিজেই দিয়েছিলাম—পারুক না পারুক গিয়ে তাকে বলা উচিত। বলব। আর কেনই বা মুছে ফেলতে পারবে না? কিন্তু তবু যেন বাধোবাধো ঠেকছিল। কি ক’রে বলব তোমার ঠাকুরদা’র ঠাকুরদা আমার প্রপিতামহের প্রজা ছিলেন, অনুগত জন ছিলেন, তাঁর ঔদ্ধত্যের জন্য আমার প্রপিতামহ তাকে একরকম খুন করিয়েছিলেন। এবং ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্ন যদি তোলো তো বলতে হয় ন্যায়-অন্যায় বিচার থাক, তবু বলতে হবে অন্যায় জেদ আবদার এবং অশোভন ঔদ্ধত্য প্রথম থেকে ঠাকুরদাস পালই দেখিয়েছেন। ওই পিদ্রু গোয়ানের বোন—তার নাম ছিল ভায়োলেট, সে নাকি বিচিত্রভাবে পেয়েছিল তার পোর্তুগীজ পিতৃপুরুষের রূপ; তার ছিল অনেকটা ফিরিঙ্গী মেয়ের চেহারা, পোড়া সাদা রঙ, নীল চোখ, পিঙ্গল চুল; আর প্রকৃতিতে ছিল চঞ্চল দুর্দান্ত। পনের-ষোল বছরের কিশোরী। রত্নেশ্বর রায়ের বড় ছেলে দেবেশ্বরের কথা শুনেছ; আমাকে দেখে আমার মেজঠাকুরদা বলেছিলেন—তিনি ছিলেন রায়বংশের শ্রেষ্ঠ সুপুরুষ। ওই দেখ তাঁর ছবি।
সুরেশ্বর উঠে গিয়ে একখানা ছবির সামনে দাঁড়াল, সুলতা তাকালে ছবিখানার দিকে। সত্য কথা বলেছে সুরেশ্বর। সত্যই দুর্লভ সুপুরুষ।
মনে পড়ল সুলতার-সুরেশ্বর বলেছে একটু আগে যে ওর মেজঠাকুরদা বলেছিলেন ওকে—তাঁর থেকেও তুমি যেন সুপুরুষ হে!
না—তা নয়। সে কথা সুলতা মানতে পারবে না। তবে সুরেশ্বরের মধ্যে তাঁর আদল আছে। উজ্জ্বল দীপ্ত মুখ, রায় বংশের চোখ বড় বড় কিন্তু দৃষ্টি তাদের উগ্র। এঁর চোখে উগ্রতা নেই, মাধুর্য এবং কৌতুকের একটি সংমিশ্রণ রয়েছে চোখে। তাও খানিকটা সুরেশ্বরের আছে, কিন্তু সেও এঁর মত নয়।
—দেখেছ!
—হ্যাঁ। হাসলে সুলতা। জমিদার ধনীর ছেলের প্রতীক বলা যায়।
সুরেশ্বর বললে—হ্যাঁ, তা বলতে পার, সেকালের খুব প্রগ্রেসিভ মানুষ। পৃথিবীর সমস্তকে শুধু ব্যঙ্গই করতেন না, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকের বঙ্গ সংস্কৃতির যে ভাগটা খাঁটি বিলেতি সভ্যতার উপাসনা করতেন, তাঁদের মধ্যে এক খণ্ড হীরকের মত উজ্জ্বল মানুষ ছিলেন। কিন্তু সে কথা পরে বলব। এখন এই ছবিটা দেখ সুলতা, এই ‘ভায়লা পিক্রস’–ভায়োলেট! অবশ্য আমার কল্পনা করে আঁকা। ঠিক সে কেমন ছিল জানি না, তবে একটু আগে বলেছি ‘কুইনি’ নামে একটি তের-চৌদ্দ বছরের মেয়েকে দেখেছিলাম গোয়ানদের সমাজনেত্রী হিলডার সঙ্গে। কলকাতায় মা-বাপ মরে যাওয়ায় এখানে এসেছে। বাপ ছিলেন একজন বাঙালী ক্রীশ্চান। মুখার্জি। সে হল ভায়োলেটের মেয়ের ছেলের মেয়ে। তার চেহারাটা নিয়েছি। কিন্তু রঙে উগ্রতা দিয়েছি। কুইনির চোখে হারমাদী পূর্ব-পুরুষের চোখের আভাস আছে, তাকে আরও নীল করে দিয়েছি। পরনে দিয়েছি নাইনটিন্থ সেঞ্চুরির ফিরিঙ্গী মেয়েদের পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত ঝোলা ফ্রক।
সুলতা বললে—কিন্তু কোমর চেকে পিঠ থেকে হিন্দুস্থানী মেয়েদের মতো ওড়না দিয়েছ কেন?
—তার কারণ সেকালে গোয়ানপাড়ায় ওরা ওইভাবে ওড়না ব্যবহার করত। সে কথা পরে বলব সুলতা। এখন আসল কথায় আসতে দাও। রাত্রির পরমায়ু ফুরিয়ে আসছে। সকালে তোমাকে চলে যেতে হবে। এর মধ্যে আমার সব কথা—রায় জমিদারদের জবানবন্দী-শেষ হবে না জানি। তুমি মাইনে করা আদালতের বিচারক নও, তুমি বিনা মাইনেতে দেশের কাজ কর, মাইনে নিয়ে কলেজে পড়াও। কাল তুমি আসবে না। তবু যতটুকু পারি ততটুকু বলে নি।
এই ভায়োলেট মেয়েটি তখন নিরুদ্দেশ হয়েছে কিছুদিন। গোয়ানরা যে গোয়ানরা ক’ বছর আগে পর্যন্ত নদীতে ডাকাতি করেছে, যাদের পূর্বপুরুষরা ত্রাসের সৃষ্টি করেছিল দেশে, শুধু লোকের সম্পদই লুটত না, ছেলে-মেয়ে যুবক-যুবতী লুঠে নিয়ে গিয়েও বেচে দিয়ে আসত; তাদের মেয়েরা নিরুদ্দেশের সঙ্গে তাদের কোন ছেলে নিরুদ্দেশ হলে তারা রাগ করত, কিন্তু তা না হ’লে তাদের মর্যাদাহানি হত এবং তারা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠত। খুঁজত কার সঙ্গে পালাল। সংসারে জাতই বোধহয় ইজ্জতের সিংহাসন বল সিংহাসন, বেদী বল বেদী।
ঠাকুরদাস পালের মৃত্যুদিনের বৃত্তান্ত ডায়রী থেকে আবিষ্কার করতে গিয়ে প্রতিটি পাতা আমাকে পড়তে হয়েছিল। এর মধ্যে পেয়েছিলাম—রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায় হঠাৎ কলকাতায় গিয়ে আবিষ্কার করেছিলেন এই ভায়োলেটকে। এই জানবাজারের বাড়ীর বন্ধ দরজায় সে মাথা কুটছিল আর চীৎকার করে ডাকছিল রায়বাহাদুরের জ্যেষ্ঠপুত্র দেবেশ্বর রায়বাবুকে।
ঘটনাটা তিনি জেনেছিলেন তার কাছ থেকে। মেয়েটা প্রেমে পড়েছিল নবীন এই রায়- বাবুর। নবীন রায়বাবুও তাকে চেয়েছিলেন বিলাসের জন্য। নবীন রায়বাবুর আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেছিল গোপালচন্দ্র পাল। ঠাকুরদাস পালের দ্বিতীয় পক্ষের জ্যেষ্ঠপুত্র। ঠাকুরদাস পাল যেমন ভালবাসত রত্নেশ্বর রায়কে, গোপালও তেমনি ভালবাসত দেবেশ্বর রায়কে। দেবেশ্বরের ছিল সে গোপালদাদা।
রায়বাহাদুর এদিনের ডায়রীতেও লিখেছিলেন—এ বংশের উপর পরমাপ্রকৃতি পরমেশ্বরীর কাছে অপরাধের এ মহাঅভিশাপ আমার আজন্মের কৃচ্ছ্রসাধন তপস্যাতেও শান্ত হয় নাই। সে অভিশাপ আসিয়া ফলিয়াছে আমার পুত্রের মধ্যে। ইহা হইতে কি নিষ্কৃতি নাই? আমি বন্ধ দরজায় সজোরে করাঘাত —অবশেষে পদাঘাত করিতে লাগিলাম। ভিতর হইতে সাড়া কেহ দিল না। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই গৃহমধ্য হইতে বন্দুকের শব্দ উঠিল।
সুলতা, বাপের ভয়ে দেবেশ্বর রায় বন্দুকে টোটা পুরে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন। চেয়ারে বসে কার্টিজ পোরা বন্দুকের নল বুকে লাগিয়ে পা দিয়ে ট্রিগার টেনেছিলেন। নড়া-চড়ার মধ্যে নলটা বুক থেকে সরে এসেছিল একপাশে। ফলে গুলিটা বগলের দিকে মাংস ভেদ করে বেরিয়ে গিয়েছিল।
তারপর দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে রায়বাহাদুর দেখেছিলেন, পাশে বন্দুক নিয়ে ছেলে পড়ে আছে রক্তাক্ত দেহে।
ভায়লাও এসেছিল—সে বুক চাপড়ে কেঁদে আছড়ে পড়েছিল।
পাওয়া যায়নি গোপালকে, সে ভয়ে রান্নাঘরের একতলা ছাদের উপর থেকে ঝাঁপ দিয়ে পাশের গলিটাতে পড়ে পালিয়ে গিয়েছিল।
সুরেশ্বর কয়েক মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে যেন তার জবানবন্দীতে একটা ছেদ টেনে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে।
সুলতা এতক্ষণ প্রায় নির্বাক হয়ে ধৈর্য ধরে শুনে আসছিল। এবার সে একটু চকিত হয়ে বললে—দেবেশ্বর রায়? কথা শেষ করতে পারলে না।
সুরেশ্বর বললে—বেঁচেছিলেন। পায়ে ট্রিগার টিপবার সময় বন্দুকটার নল খানিকটা ঝাঁকিতে খানিকটা নড়েচড়ে স’রে গিয়েছিল। বলেছি সে কথা। তিনি না বাঁচলে আজ সুরেশ্বর রায় পৃথিবীতে এসে এই ১৯৫৩ সালের নভেম্বরের রাত্রে জমিদারী উচ্ছেদ আইন পাস উপলক্ষ করে তোমার সামনে জবানবন্দী দিত না। এই সব ছবি এঁকে একজিবিশন করত না। দেবেশ্বর রায়ের তখন বিবাহ হয়ে গেছে। বধূটি তৎকাল অনুযায়ী বালিকা। দেবেশ্বর ছিলেন আধুনিক। তিনি এ বিবাহে রাজী ছিলেন না। বীরেশ্বর রায়ের কালের তুলনায় সেকালে ছেলেমেয়েদের বিয়ের বয়স বাড়লেও রত্নেশ্বর রায় ছিলেন গোঁড়া মানুষ। তিনি ছেলের উনিশ বছর বয়সে একটি দশ বছরের মেয়ের বিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। দেবেশ্বর রায়ের বিয়েতে সকল কাজেই সকলের আগে ছিলেন ঠাকুরদাস পাল। বিয়ের গায়ে হলুদের তত্ত্ব নিয়ে গেছেন তিনি, বর কনে যখন কীর্তিহাটে আসে বজরায় তখন তার ভার ছিল তাঁর হাতে। আর দেবেশ্বর বরাভরণ, গার্ডচেন, ঘড়ি, হীরের বোতাম, দু হাতের চারটে দু হাজার টাকা দামের আংটি, তাঁর এসেন্স-পমেটম থেকে সমস্ত বিলাসদ্রব্যের ভার ছিল ঠাকুরদাসের বৃদ্ধ বয়সের পুত্র আদরের গোপালের উপর।
সুলতা একটু হাসলে।
সুরেশ্বর প্রশ্ন করলে—তুমি হাসলে সুলতা?
—তুমি আমার কাছে আস নি সেদিন ফিরে, সে ভালই করেছিলে।
—কেন?
—আমার ঠাকুরদার কাকা তোমার ঠাকুরদার খানসামা ছিলেন। ঠাকুরদাস পালকে খুন করার ঘটনা—তিনি তোমার পূর্বপুরুষের প্রজা ছিলেন এ ঘটনাটা বিচার করে যদি বা ভুলে গিয়ে পথ পাওয়া যায়, এই কথাটা ভুলতে পারার আর পথ নেই!
সুরেশ্বর চুপ করে রইল। একটু পরে বললে-আমি ভুলতে পারতাম। ভুলতে পারতাম এ কথাই বা বলছি কেন—কথাটা আমার মনেই হয় নি।
—না হতে পারে। আমার মনে হত। কারণ যারা বড় ছিল, তারা ভুলতে পারে কিন্তু যারা ছোট ছিল তারা ভুলতে পারে না। যাক, কথা তোমার শেষ কর। আমি শুধু জানতে চাচ্ছি কি কথা তিনি প্রকাশ করে দিতে ভয় দেখিয়েছিলেন, তিনি মানে ঠাকুরদাস পাল, যাতে রায়বাহাদুর এমন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন। যা তিনি ডায়রীতে লেখেন নি। তবে একটা কথা বলেছ, রায়বাহাদুর লিখেছেন ডায়রীতে, অদৃষ্টের চক্রান্তে বিস্ময় প্রকাশ করে লিখেছেন —অদৃষ্টের চক্রান্তে আমি আজ পোষ্যপুত্র হয়ে ফিরে এলাম আমার জন্মদাতা ও গর্ভধারিণীর সন্তানরূপে। বিমলাকান্ত কি চুরি করেছিলেন এঁদের সন্তানকে? না—।
কথায় প্রশ্ন না করে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সে।
সুরেশ্বর হেসে বললে না—তিনি করেন নি।
—তবে?
—করেছিলেন বিমলা দেবী। বীরেশ্বরের সহোদরা। যাঁর সন্তান হয়ে হয়েই মারা যেত। একদিন পুরো নয়—ঘণ্টা দশেক আগে-পিছু রায়বাড়ীতে দুটি সন্তান এসেছিল। আগে বিমলার সন্তান এল, তারপর ভবানী দেবীর। দ্বিতীয় দিনে বিমলার সন্তানের অসুখ হল। যেমন অসুখ হয়ে তার সব সন্তানগুলো গেছে। যেমন যেত বিমলা দেবীর মা সোমেশ্বর রায়ের স্ত্রী রাজকুমারী কাত্যায়নী দেবীর। যিনি রূপের ভাণ্ডার নিয়ে এসে রায়বাড়ীতে রায় বংশের প্রতিষ্ঠা করেছেন। বিমলা ছিলেন পাগল। অন্তর্বত্নী হলেই তাঁর পাগলামি ভাল হত। সন্তান হয়ে মারা গেলে আবার পাগল হতেন। তিনি তাঁর ছ-আনা অংশের সম্পত্তি কে ভোগ করবে এ ভাবনাতেই পাগল হতেন হয়তো। তিনি গভীর রাত্রে তাঁর নিজের রুগ্ন সন্তান নিয়ে ভ্রাতৃবধূর ঘরে ঢুকে সন্তান বদল করে নিয়ে যান। কিন্তু তাঁর খেয়াল ছিল না যে সেই গভীর রাত্রে বীরেশ্বর রায় লুকিয়ে সুতিকাঘরে ঢুকেছিলেন—সন্তানের মুখ দেখতে।
বীরেশ্বর রায়—বীরেশ্বর রায় হলেও কালটা সেকাল। লজ্জায় বীরেশ্বর রায় হয়েছিলেন অন্তরালবর্তী। ভবানী দেবীও চোখ বুজেছিলেন লজ্জায়। তাঁরা ভেবেছিলেন পাগল বিমলা দেবী নিজের সুতিকাঘর ভেবেই ঢুকেছেন—এই বাড়ীতেই সেটা সুলতা। তুমি তো দেখেছ মাঝখানকার যে হলটা যে হলটায় বীরেশ্বর রায় বসতেন—তার এপাশ থেকে যে করিডোরটা অন্দরে গেছে, তার প্রথমেই দু পাশের দুখানা ঘরে ঘটেছিল এই ঘটনা। সামনাসামনি ঘর। এ দু’ঘরেই দুজনের সুতিকাগার। বিমলা দেবী চোরের মতো ঘরে ঢুকে নিজের রুগ্ন ছেলেকে নামিয়ে দিয়ে বীরেশ্বরের পুত্রকে তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন।
ভবানী দেবী—বীরেশ্বর রায় দুজনের কণ্ঠ থেকে একটি শব্দ বের হয়নি, হ’তে পারেনি। ভবানী দেবী রুগ্ন ছেলের পাশে পাথরের মূর্তির মত বসে ছিলেন। বীরেশ্বর অধীর হয়ে উঠেছিলেন। হঠাৎ বিমলাকান্ত এসে তাকে বলেছিলেন-শান্ত হও বীরেশ্বর, আমি সব শুনেছি। শুনেছি কেন, আমিও দেখেছি। সুতিকাঘর দুটির পাশেই ছিল বীরেশ্বর রায় এবং বিমলাকান্তের শোবার ঘর। রায়বাড়ীতে এ ব্যবস্থা রাজকুমারী কাত্যায়নী দেবীর আমল থেকে। তিনি যখন দশ বছর বয়সে রায়বাড়ী আসেন, তখন থেকেই তিনি সংসারের গৃহিণী। তাঁর নিজের সন্তান হয়ে বাঁচত না। বেঁচেছিল তান্ত্রিক শ্যামাকান্তের তন্ত্রমন্ত্রে কি ক্রিয়াকর্মের ফলে। কাত্যায়নী দেবী স্বামীকে পাশের ঘরে শুইয়ে রাখতেন। সোমেশ্বর রায়ও শুতেন। কারণ শোকের মুহূর্তে কাত্যায়নীর পাশে না থেকে তিনি পারতেন না।
নিজের কন্যার প্রথম সন্তান যখন মরল, তখন তিনিই এ ব্যবস্থা করেছিলেন। অথচ যখন কন্যা প্রথম পাগল হয়, তখন তাকে কীর্তিহাটে আনবার সময়, তিনি জামাতার জন্য দাসীর ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলেন।
হাসলে সুরেশ্বর।
তারপর বললে—যা বলছিলাম, যা প্রশ্ন করেছ তার কথাই বলি সুলতা। রাত্রি বুঝি শেষ হয়ে আসছে। বিমলাকান্ত বীরেশ্বরকে বলেছিলেন—তুমি শান্ত হও বীরেশ্বর, আমি সব দেখেছি। কাল যখন রাত্রে ভবানী বউমার ঘর থেকে ছেলে তুলে নিয়ে এল, তখনই আমি গিয়ে ওর সামনে দাঁড়িয়েছিলাম। মেঝেতে এগুনিটা অঘোর ঘুমুচ্ছে। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বিমলা বিবর্ণ হয়ে গেল। আমার মনে হল, হয়তো অজ্ঞান হয়ে যাবে। তবু আমি যাই নি। দাঁড়িয়েই ছিলাম। যাক, অজ্ঞান হলে আমি অন্তত তোমার সন্তান তোমাকে ডেকে জাগিয়ে দিয়ে আসতে পারব। কিন্তু কিছুক্ষণের পর নিজেকে সামলে নিয়ে বিমলা বললে—যাও, তুমি শোও গে। নইলে চেঁচিয়ে আমি গোল করব। বলব- আমার আঁতুড়ে ঢুকছে। আমি বললাম-কি করলে? বিমলা বললে—বেশ করেছি। আমার ভাগের সম্পত্তি খাবে কে? বললাম—ওই ছেলেই খাবে। বললে—হ্যাঁ খাবে, আমার ছেলে হয়ে খাবে।
বীরেশ্বর আশ্বস্ত হয়েছিলেন। বিমলা দেবীর সন্তান ভবানী দেবীর সুতিকাঘরে মারা গিয়েছিল। লোকে বলেছিল, এবার কাত্যায়নী দেবীর মৃতবৎসা রোগ মেয়েকে ছেড়ে ছেলের বউকে ধরল। সোমেশ্বর রায় জেনেছিলেন। তাঁকে বলেছিলেন বীরেশ্বর এবং বিমলাকান্ত। সোমেশ্বর বলেছিলেন-তোমার আরও সন্তান হবে বীরেশ্বর। ওর আর হবে না। হলেও বাঁচবে না। ওই ছেলেকে আমি অর্ধেক সম্পত্তি দেব। বাকী তোমার সন্তানদের মধ্যে ভাগ হবে। আর ওকে তুমি পোষ্যপুত্র নেবে। তার স্বীকারপত্র বিমলাকান্ত তোমাকে লিখে দেবে।
বীরেশ্বর বলেছিলেন—তা হ’লে ওর নাম থাকবে রত্নেশ্বর।
সুলতা তার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলে-এ তুমি কি বলছ সুরেশ্বর?
সুরেশ্বর বললে সে পত্র আমি পেয়েছি সুলতা!
—কিন্তু —? ভ্রূ দুটো কুঞ্চিত হয়ে উঠল সুলতার। বিমলাকান্ত আর দিতে চান নি? তাই
এত রাগ—
—না সুলতা। তারপর এমন বিচিত্র ঘটনা ঘটল, যাতে বীরেশ্বর রায় আর বলতে সাহস করলেন না যে ওটি তাঁর পুত্র। ছেলেটি যখন এক বছরের তখন সোমেশ্বর রায় মারা গেলেন। উইলে লিখে গেলেন- বিমলা দেবীর পুত্র সম্পত্তির অর্ধাংশ পাইবেক। কিন্তু তাহাকে রায়বংশের গোত্র ধারণ করিতে হইবেক। সেই কারণে মদীয় পুত্র তাহাকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিবেন। কিন্তু তার পর ছেলেটি যত বড় হতে লাগল, তত মনে হ’ল এ ছেলে অবিকল বিমলাকান্ত!
চীৎকার করে উঠল সুলতা—সুরেশ্বর!
তার মনে পড়ল-বীরেশ্বর রায় বার বার তাঁর স্মরণীয় ঘটনার খাতায় ভবানী দেবীকে পাপিনী বলেছেন।
ঠিক সেই সময়ে পাখী ডেকে উঠল।
কলকাতাতে পাখীরা ডাকে, গ্রামের মতো কলরব করে। ভোর হয়ে আসছে। সুরেশ্বর বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখতে গিয়ে দেখলে কাচের জানালাগুলো বন্ধ।
সে দৃষ্টি ফিরিয়ে সুলতার দিকে তাকিয়ে বললে—না সুলতা, ওই মহিমময়ী জননীটি আমাদের বংশের মহাপুণ্য। এই রাত্রি শেষ হচ্ছে। ভোরের আলো ফুটছে। উনি ঠিক এই মুহূর্তটির মত। উনি ওর পিতৃবংশে পিতা এবং স্বামী বংশে স্বামীকে বলতে গেলে উদ্ধার করেছেন।
তোমার মতো আমারও উদ্বেগের উৎকণ্ঠার আর সীমা ছিল না।
সেদিন—কীর্তিহাটে, যেদিন রাত্রে রায়বাহাদুরের ডায়রীতে, ঠাকুরদাস পালের খুন হওয়ার দিনের ডায়রী পড়ে আমি ভাবছিলাম তোমার কথা, আর বংশের যে পাপের কথা কিছুতেই লিখতে পারেন নি রত্নেশ্বর রায়—সেই কথাটির কথা। প্রায় পাগলের মত হয়ে গিয়েছিলাম। স্নান করি নি খাই নি। বার বার ডায়রী পাল্টেছি। পড়তে শুরু করেছি সেই গোড়া থেকে। মেজঠাকুমা এসে ফিরে গেছেন। তিনি উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেছেন, আমি রূঢ় কথা বলেছি। রঘুয়া আমার ভয়ে সামনে আসতে পারে নি। সন্ধ্যার সময় একবার সাহস করে অর্চনা এসেছিল—তার পিছনে মেজঠাকুমা ছিলেন।
অর্চনা বলেছিল-সুরেশ্বরদা!
রাগ হয়েছিল, সে রাগ চেপে অস্বাভাবিক গম্ভীর কণ্ঠে বলেছিলাম—নায়েব এখনও মেদনীপুর থেকে ফেরে নি অৰ্চনা।
অর্চনা মুখরা মেয়ে এবং সাহসী—তা তুমি নিশ্চয় স্বীকার করবে—সেও দমে গিয়েছিল।
একটু পর বলেছিল—ওই অতুলদা’র কথা ছাড়া আর কি কোন কথা নেই আমাদের সুরোদা?
আমি বলেছিলাম—থাকলেও এখন কোন কথা বলবার মত সময়ও নেই, মনের অবস্থাও নেই, অৰ্চনা।
অর্চনা বলেছিল—চল ঠাকুমা!
বলে সে মেজদিকে নিয়ে চলে গিয়েছিল।
রাত্রে ঘুম আসে নি। আমি সকালবেলা থেকে অতুলের দৃষ্টান্ত মনে করে সংকল্প করেছিলাম—যে মদ্যপান আর করব না। কিন্তু রাত্রে মদ্যপান করেছিলাম—ঘুমের জন্য। রঘু সভয়ে খাবার এনে নামিয়ে দিয়েছিল। ক্ষিদেও ছিল, খেয়েছিলামও। তারপর একসময় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, সুরার প্রভাবে।
এমনি ভোরবেলা ঘুম ভেঙেছিল রঘুর ডাকে।
রঘুরা এসে ডেকে বলেছিল—পুলিস!
—পুলিস?
—হ্যাঁ, গাদা গাদা। চারিদিক ঘেরাও করেছে।
চমকে উঠেছিলাম। জানালায় গিয়ে তাকিয়ে দেখেছিলাম—পুলিস গিজগিজ করছে। ঘেরাও করেছে চারিদিক। রায়বাড়ীর চারিদিক। আর্মড পুলিস।
তারাই এ সত্যগুলি আমার কাছে প্রকাশ করে দিয়ে গেল খানাতল্লাসীর সময়।
সুরেশ্বর বললে–গোটা রায়বাড়ী সার্চ করেছিল পুলিস। গতবার কেবল অতুলেশ্বরের অংশের ঘর সার্চ করে চলে গিয়েছিল। এবার গোটা বাড়ীটা।
সর্বাগ্রে সার্চ করেছিল রত্নেশ্বর রায়ের খাস কাছারি। যে ঘরটায় অতুল ওই নিষিদ্ধ ভয়ানক বস্তুগুলি লুকিয়ে রেখেছিল, সেই ঘরখানা।
আমি বিবিমহলেই বসেছিলাম। গতরাত্রি পর্যন্ত যে চঞ্চলতা, অধীরতা আমাকে অধীর করে রেখেছিল, তা ওই পুলিসবাহিনী দেখেই যেন স্থির হয়ে গেল। চিন্তা শুধু একটি। অর্চনা এবং মেজদি। মেজদির জন্যে খুব চিন্তা ছিল না। কারণ মেজদির সঙ্গে অভুলেশ্বরের ঘনিষ্ঠতা মা ও সন্তান হিসেবে। তাছাড়া তিনি ইংরেজ তাড়াবার জন্যে কোমরে কাপড় জড়িয়ে লাগবার মত প্রচণ্ডা একথা চট্ করে কেউ মনে করবে না। ভয় অর্চনার জন্যে।
মধ্যে মধ্যে প্রশ্ন করছিলাম—অতুল মারধর খেয়ে সব বলে ফেলে নি তো? বাংলাদেশে বিপ্লবের ইতিহাসে জমিদার ও ধনীর ছেলে নরেন গোসাঁই মানিকতলা বোমার মামলায় অ্যাপ্রুভার হয়ে জমিদার-সন্তানদের অবিশ্বাসী প্রমাণ করে গেছে। তার উপর এই রায়বংশ। হঠাৎ মনে হয়েছিল, ব্রজেশ্বরদার কথা। ব্রজেশ্বরদা যাবার সময় সব বলে দিয়ে যায় নি তো? অসম্ভব নয়! সে সব পারে!
ঠিক এই সময় একজন পুলিস অফিসারকে সঙ্গে করে আমার কাছে এসেছিলেন দেবোত্তরের এজমালী নায়েব। আমি একটু চকিত হয়েছিলাম নিশ্চয়। নায়েব বলেছিলেন-এ কাছারী হল এই সুরেশ্বরবাবুর।
জিজ্ঞাসা করতে হল না, অফিসার জিজ্ঞাসা করলেন—ওই কাছারীঘরখানা আপনার?
নায়েব বুঝিয়ে দিলে—ওই খাস কাছারী রায়বাহাদুরের—ওই ঘরের চাবি চাচ্ছেন।
মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠল। বুঝলাম, পুলিসের এই সার্চটির পিছনে নিশ্চিত সংবাদ আছে। নিছক সন্দেহবশে এ সার্চ নয়।
অফিসারটি বললেন—আপনি সঙ্গে আসুন, আর চাবিটা চাই।
উঠে দাঁড়ালাম, বললাম- চাবি তো আমার কাছে নেই। চারি আমার এখানকার কর্মচারীর কাছে আছে, তিনি কাল মেদিনীপুর গেছেন, ফেরেন নি।
—অতুলেশ্বরের জামিনের জন্যে গেছে?
—হ্যাঁ।
—উনি আপনার কে?
—কাকা। আমার বাবার আপন খুড়তুতো ভাই।
—আপনারা তো পৃথক।
—হ্যাঁ। অনেক দিন থেকে।
—তবে?
—পাঠিয়েছি, আমার কর্তব্য বলেও বটে, আর এমন কোন মারাত্মক অপরাধ সে করে নি, এটা আমার বিশ্বাস বলেও বটে।
—ও আচ্ছা। আসুন। তালা তাহলে ভেঙেই ফেলতে হবে। সার্চের সময় আপনি উপস্থিত থাকবেন।
আমার আজ বয়স চুয়াল্লিশ, ১৯১০ সালে আমার জন্ম। ১৯৩৬ সালে আমার বয়স ছিল সাতাশ। বাবা বিবাহ করেছিলেন ১৯০৮ সালে। তারপরই তিনি এসব মেরামত করিয়েছিলেন। সে মেরামতের সময়েই এ ঘর মেরামত হয়েছিল। এবং সেই সময় থেকেই আর খোলা হয় নি। কড়া হুকুমে বন্ধ ছিল। কারণ এই মেরামতের বছর কয়েক আগে মেজঠাকুরদার এ কন্যার বিবাহে এ ঘর খুলে দেওয়া হয়েছিল বরযাত্রীদের ব্যবহারের জন্যে। বরযাত্রীরা এ ঘরে উপদ্রবের বাকী রাখে নি। পুরনো আমলের ঝাড়লণ্ঠনগুলো লাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে ভেঙে দিয়েছিল। একখানা মূল্যবান পুরনো গালিচা ক্ষুর দিয়ে কেটে দিয়ে গিয়েছিল। তারপর থেকে এ ঘর ব্যবহার সম্পর্কে তাঁর যে কড়া নির্দেশ তা কখনও শিথিল হয়নি। এবং মেজতরফ যতই অভাবে পড়ে ছোট কাজ করে থাক, এদিকে তাদের আভিজাত্যের উঁচু মাথা কখনও হেঁট করেন নি। এ খাস কাছারীর সীমানা তাঁরা মাড়াতেন না। নিষেধ ছিল। শুধু অতুলেশ্বর জানলার শিক সরিয়ে ওই জিনিসগুলো রাখতে এ ঘরে ঢুকেছিল গোপনে। সেই পথেই আমি ঢুকেছিলাম সেদিন রাত্রে চোরের মত।
পুলিস অফিসারদের হুকুমে হাতুড়ি পিটে পুরনো মরচে ধরা তালাটা ভেঙে ফেলে, কনেস্টবলেরা বুটের লাথিতে খুলে দিল দরজাটা। মোটা ভারী সেগুন কাঠের দরজা দুটোও দীর্ঘকাল বন্ধ থেকে যেন জমে গিয়েছিল। প্রবল ধাক্কায় খুলবার সময় এক পাল্লা দরজার একটা কব্জা ভেঙে গেল। সাতাশ বছরের বদ্ধ হাওয়া একটা গন্ধ নিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে।
দরজা-জানলা খুলে সার্চ আরম্ভ হল। আমি সার্চের দিকে দৃষ্টি রাখতে পারিনি। আমি ও-বিষয়ে একরকম ভবিতব্যের উপর নির্ভর করে একরকম নিশ্চিন্ত; হ্যাঁ, তাছাড়া আর কি বলব বল? তাই ছিলাম। আমার দৃষ্টি পড়েছিল রায়বাহাদুরের ছবির দিকে। তাঁর মাথার উপর কুইন ভিক্টোরিয়া এবং প্রিন্স অ্যালবার্টের ছবি! রায়বাহাদুরকে আমি ব্যঙ্গ করিনি। আমি তাঁর ছবি দেখে বীরেশ্বর রায়ের ছবি দেখে মেলাচ্ছিলাম, দুজনের মধ্যে মিল কতখানি, অমিল কতখানি। অমিল বেশী কিন্তু তার মধ্যেও আশ্চর্য মিল চোখের চাউনিতে এবং নাকের গড়নে। নাক আর চোখ এ দুটোর সঙ্গে সম্বন্ধ বড় নিকট।
ওদিকে শতরঞ্জি উঠিয়ে বালিশের গাদা তছনছ করে তার তুলো ছড়িয়ে ঘরটা কয়েক মিনিটের মধ্যে একটা ধুলোর ঘূর্ণি তুলে দিলে। গোটা বিশ-পঁচিশ ইঁদুর ঘরময় ছুটোছুটি করে বেরিয়ে গেল। কিন্তু পাওয়া কিছু গেল না। এমন কি সেই ছেঁড়া বালিশটা, সেটাও নেই। সেটা বিছানার গাদার উপরেই ছিল। একটু বিস্মিত হলাম।
মনের মধ্যে অর্চনার মুখটা ভেসে উঠল। তাছাড়া আর কে হতে পারে?
পুলিসের সার্চ অদ্ভুত সুলতা। তারা দেওয়াল থেকে বড় বড় অয়েল পেন্টিংগুলো পর্যন্ত নামিয়ে দেখলে। ঘরের দেওয়াল ঘেঁষে এক সারি কুশন দেওয়া চেয়ার ছিল, সেগুলো পরীক্ষা করে দেখলে। ঘরের পিছনদিকে যে জানলাটার শিক খোলা যেত, সেটা তারা গোড়াতেই আবিষ্কার করেছিল।
একজন অফিসার বললেন—কেউ নিশ্চয় সরিয়েছে এর মধ্যে। ধুলোর উপর যেন আসা- যাওয়ার চিহ্ন রয়েছে।
—পরশুই সার্চ করা উচিত ছিল।
—খোলো, ওই ঘর দুটো খোলো।
হলঘরটার দুপাশে দুটো ছোট কামরা। বন্ধ দরজা দুটোর একটায় তালা ঝুলছিল, কিন্তু তালাটা খুলে গেছে। সেদিন রাত্রে ওটা লক্ষ্য করিনি!
তালাটা টেনে ছাড়িয়ে ফেলে ঘরে ঢুকল পুলিস।
ঘরখানা ছিল রায়বাহাদুরের খাস কামরা, তিনি এই ঘরে বসে কাজ করতেন। সেক্রেটারীয়েট টেবিল, চামড়ার গদী-আঁটা পুরনো আমলের চেয়ার দিয়ে সাজানো, পাশে একটা প্রকাণ্ড সে-আমলের মেহগনি কাঠের ইজিচেয়ার, দুই কোণে দু প্রকাণ্ড দামী কাঠের সিন্দুক। সিন্দুক দুটোর আলতারাপ দুটো মরচে ধরে নষ্ট হয়ে গেছে।
সেক্রেটারীয়েট টেবিলটার ড্রয়ারগুলো খোলাই ছিল। এবং তার মধ্যে ছিল কয়েকটা পুরনো জিনিস, একটা ভাঙা পেপার-ওয়েট, দুটো কলম, আলপিন কুশন, আর একটা আতরের শিশি। কিছু শুকনো ফুল বিশ্বপত্র, সম্ভবতঃ সেগুলো নির্মাল্য। আর একটা ধুলো-মাখানো ছোট পাথর, নীল কাঁচের মতো এক কোণে পড়েছিল। সেটা আমি হাতে পরেছিলাম সুলতা, সেটা ছিল মূল্যবান নীলা। তার কথা থাক। পরে যদি কোন দিন সময় করে এস, তবে তোমাকে বলব। এসবগুলো পুলিস দেখেও দেখেনি, এতে তাদের প্রয়োজন ছিল না। আমি ওগুলো পরে সংগ্রহ করেছিলাম।
পুলিস ড্রয়ার বন্ধ করতে গিয়ে আধখোলা রেখেই ছেড়ে দিয়ে খুলেছিল ওই ভাঙা দুটো সিন্দুকের একটা। একটা কৌতুক ঘটেছিল। কৌতুক ছাড়া কি বলব। ছোট-বড় গোটা দশেক কাঁকড়া বিছে সিন্দুকটার খোলা ডালার গায়ে লেগেছিল; তার আলোর ছটায় আর মানুষের সাড়ায় কিলবিল করে নড়াচড়া শুরু করে, ও-ঘরের ইঁদুরগুলোর মতই চারিদিকে পড়ল ছড়িয়ে। সে সিপাহীটা ডালা খুলেছিল, সে আয় বাপ! বলে ডালাটা ছেড়ে দিয়ে পিছিয়ে এসে পড়েছিল একজনের ঘাড়ে। সে আর একজনের। সঙ্গে সঙ্গে সে এক তাণ্ডব। কে. পালাবে আগে তাই নিয়ে হুড়োহুড়ি। কিন্তু সে মিনিটখানেকের জন্য। তারপরই পুলিস-অফিসার দুজন একসঙ্গে ধমক দিয়ে উঠতেই তারা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে বুট দিয়ে চেপে মেঝের উপর ছড়িয়ে পড়া কয়েকটা বিছেকে পা দিয়ে চেপে মেরে দিলে এবং কয়েকটা সিন্দুকের তলায় গিয়ে লুকোলো।
পুলিস-অফিসার এবার এগিয়ে এসে নিজেই ডালাটা তুলে ধরলেন। তখন ডালা থেকে নেমে তারা বোধহয় সিন্দুকের ভিতরে থাকবন্দী সাজানো কাপড়ে বাঁধা কাগজের দপ্তরের ভিতর লুকিয়েছে। দুটো-তিনটে তখনও দপ্তরের ফাঁকে উপরের দিকেই ছিল, তারা লেজের দিকটা বেঁকিয়ে তুলে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে রয়েছে।
ভিতরের দপ্তরগুলোর দিকে তাকিয়ে অফিসারটি বললেন—এর মধ্যে কিছু থাকবে কি? এত কাঁকড়া বিছে?
অন্য অফিসারটি বললেন—দাঁড়াও জিজ্ঞাসা করে আসি।
এবার ইউরোপীয়ান অফিসার এসে সব দেখে বললেন—দেখতে নিশ্চয় হবে। You must; information is definite. You must.
একটু ভেবে নিয়ে বললেন—ইস্কো বাহার নিকালো। দোনোকো।
অর্থাৎ গোটা সিন্দুক দুটো।
তাই হল। সায়েব আমাকে প্রশ্ন করলেন—কি আছে এতে? কি এগুলো? ছড়ি দিয়ে দপ্তরগুলোকে দেখিয়ে দিলেন।
বললাম-আমি জানি না!
—জানি না? এ ঘর তোমার নয়?
—হ্যাঁ আমার। কিন্তু আজ আমি প্রথম ঢুকছি এই ঘরে। শুনেছি এ ঘর তালাবন্ধ আছে আমার জন্মের আগে থেকে!
—মানে?
মানে সংক্ষেপে যতটা বলা যায় বললাম। সাহেব বললেন—আই সী!
বাইরে সিন্দুক দুটো টেনে এনে, ডালা খুলে উল্টে ফেলে দিলে। ভিতরের দপ্তরগুলো বেরিয়ে পড়ল মাটির উপর। তারপর লাঠি দিয়ে ঠেলে দপ্তরগুলো নাড়া দিয়ে কাঁকড়াবিছের সঙ্কট-মুক্ত করে একটি একটি করে সরিয়ে দেখলে।
এবার বাইরের পূর্ণ রৌদ্রালোকে দপ্তরগুলোকে দেখা গেল ভাল ক’রে। তিনজন অফিসার তিনটে দপ্তর তুলে নিয়ে সন্তর্পণে খুলে দেখলেন।
সুলতা, তারই মধ্য থেকে বের হ’ল-আমি যা খুঁজছিলাম তাই। যা বীরেশ্বর রায়ের স্মরণীয় ঘটনার খাতায় নেই, যা রায়বাহাদুরের রত্নেশ্বর রায় ডায়রীতে লেখেন নি, তাই সব পেলাম ওই দপ্তরের মধ্যে। রায়বংশের গোপন কলঙ্ককথা বল তাই, অথবা বৈদগ্ধ্যের চকমিলান মহলে আঁধার সুড়ঙ্গ বল তাই।
সুলতা বললে—পাখী ডাকছে—সুরেশ্বর। সকাল হতে দেরী নেই—
সুরেশ্বর বললে—ভুলিনি সে কথা। তবু কথাগুলো এসে পড়ল। এই কথাটাই ভেবে এসেছি এতকাল। কিন্তু সে থাক। এখন সেদিনের কথাই শেষ করে নিই। হ্যাঁ, সেদিন যে দপ্তরটা সাহেব দেখছিলেন, সে দপ্তরে বাঁধা কাগজগুলির কোনটি কোন হিসেবের কাগজ নয়—বিষয়ের কাগজ ছিল না, সবগুলি চিঠি। সায়েবটি যে দপ্তরটা খুলেছিলেন তার একখানা চিঠি দেখে বললেন—
My God! Letters—very old letters—।৪57, September, it is from the District Magistrate of Midnapur to Bireswar Roy. I see.
কিছুটা পড়ে রেখে দিয়ে বললেন –in ।৪57 these people thought that the Britishers were godsent to this country to save them from the tyrants-Rajas, Maharajas and Nawabs of Bengal and also the Burgee Plunderers from the south, and in ।936 their children are trying to overthrow the same British Goverment. Ungrateful creatures.
আমার দিকে তাকিয়ে বললেন —Hallo young chap, take this letter. Just read it.
বলে দপ্তরটাসুদ্ধ আমার দিকে ছুঁড়ে দিলে।
চিঠিখানার কথাই আগে বলি সুলতা। চিঠিখানা মেদিনীপুরের ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট লিখেছিলেন বীরেশ্বর রায়কে। বীরেশ্বর রায়ই প্রথম চিঠি লিখে তাঁকে জানিয়েছিলেন—তিনি কীর্তিহাটে এই সিপাহী বিদ্রোহের দুর্দিনে এসেছেন—এখানে যাতে কোন হাঙ্গামা না হয়, উত্তর ভারতের অপরিণামদর্শী অকল্যাণকর উত্তেজনার প্রচার এবং প্রসার না ঘটে তাই দেখবার জন্য। কলকাতার ১৪ই জুনের অবস্থা তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন। নিদারুণ উৎকণ্ঠা ভোগ করেছেন। নবাব ওয়াজিদ আলি শা ও তাঁর দুজন মন্ত্রীকে ফোর্ট উইলিয়মে বন্দী করা হয়েছে। কলকাতার ধনী শিক্ষিত সম্প্রদায় সকলেই এই অবস্থায় অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত। তাঁদের সকলেই একবাক্যে সঙ্কল্প গ্রহণ করেছেন যে, এই বর্বর সিপাহীগণের এবং অন্য প্রদেশের কতিপয় অবিবেচক স্বার্থান্ধ অত্যাচারী রাজা ও জমিদার এর সুযোগ নিয়ে উত্তরভারতে যে সর্বনাশা নরকাগ্নি প্রজ্বলিত করেছেন, সেই অগ্নির বিস্তার যাতে এই শান্ত ইংরাজানুরাগী বঙ্গদেশে না হয় তার জন্য প্রাণপণ সমবেত চেষ্টা করতে হবে। আমি মেদনীপুরে আমার স্বগ্রামে ও আমার জমিদারী এলাকায় থেকে বেশী কাজ করতে পারব ব’লেই এসেছি এবং অবিলম্বে আমার আসার সংবাদ এবং উদ্দেশ্য আপনাকে জ্ঞাত করা কর্তব্য বোধ করছি। এবং নিবেদন করছি যে, অত্র অঞ্চলে সুসভ্য সুশৃঙ্খল এই ইংরাজ শাসন উচ্ছেদ করবার চেষ্টা যারা করবে তাদের উপর দৃষ্টি রাখাই আমার সংকল্প, এবং সর্ববিধ সংবাদ মাননীয় মহোদয়কে জ্ঞাত করব। অত্র জেলায় পাইক ও চুয়াড় বিদ্রোহ এবং এই কিছুদিন পূর্বে জঙ্গল অঞ্চলে সাঁওতাল বিদ্রোহের কথা স্মরণ ক’রেই একথা মাননীয় মহোদয়ের নিকট নিবেদন করলাম।
ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ঠিক এই কথাগুলিই লিখে বীরেশ্বর রায়কে ধন্যবাদ দিয়ে লিখেছিলেন —এসব তথ্য সত্য হলেও ইংরাজ শাসনশক্তি অত্যন্ত সুদৃঢ়। এসব উচ্ছৃঙ্খল শয়তানদের দমন করতে আমরা বদ্ধপরিকর। তোমার এই পত্রে অবশ্যই আমি আনন্দিত হয়েছি, উৎসাহিত বোধ করেছি। কীর্তিহাট জমিদারদের রাজভক্তির কথা সুবিদিত। আমি অত্যন্ত সুখী হয়েছি যে, তুমি এই সঙ্কটের সময় আপনার শক্তির স্বক্ষেত্রে চলে এসেছ। এবং সক্রিয়ভাবে সরকারকে সাহায্য করতে কাজ করছ, বিশ্বস্তভাবে কাজ করছ জেনে খুশী হয়েছি। ভবিষ্যতে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরে এলে সরকার অবশ্যই এ কথা মনে রাখবেন।
দপ্তরটায় বেশীর ভাগ সরকারী চিঠিপত্র। বীরেশ্বর রায়ের আমলের। রায়েরা সে আমল থেকেই শুধু বিষয়-সংক্রান্ত চিঠিপত্র নিয়মিতভাবে ফাইল করার মতো থাকে-থাকে সাজিয়ে রাখেন নি, বন্ধুবান্ধবদের চিঠিপত্র তাও রেখে গেছেন। বিখ্যাত রাজনারায়ণ বোসের খানকয়েক চিঠিও পেয়েছিলাম।
ওদিকে তখন দু নম্বর সিন্দুকটা বের করে এনে খোলা হল। সে সিন্দুকে বের হল সব বিচিত্র জিনিস। জড়িবুটি নির্মাল্য থেকে নানান জিনিস; শিলাজতু, মৃগনাভি, রাশীকৃত খালি আতরের শিশি, সে আমলের দামী বিলিতী এসেন্সের শিশি, সমস্ত কিছুতে পুরনো আমলের ডগডগে কালিতে নামলেখা কাগজ আঁটা। জড়িবুটির মোড়কেও নাম লেখা আছে। একটা বিচিত্র নাম আমার মনে আছে—’রেসা খাদমে’—তার তলায় লেখা আমাশয়ের অব্যর্থ ঔষধ। এ ছাড়া বেরিয়েছিল কতকগুলো ছোরা।
পুলিস অফিসারেরা উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু ছোরাগুলির বাঁটে কাগজ আঁটা—তাতে লেখা ছিল—’চিতোরের রাজপুত ছোরা’, ‘মোগল বাদশাহ বংশের ছোরা’; ‘মুরশিদা- বাদের নবাব বংশের ছোরা’; এই তিনটেই পড়া গিয়েছিল, বাকীগুলোর লেখা বিবর্ণ হয় নি কিন্তু কাগজ ছিঁড়ে দু’একটা অক্ষর ছাড়া বাকীটা ছিল না।
আর পাওয়া গিয়েছিল—ছোট বড় মাঝারি সাইজের দক্ষিণের পিতলের এবং পাথরের পুতুল। শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন। কিছু পাওয়া গিয়েছিল নানা আমলের তামা ও রুপোর টাকা।
একটি স্ফটিকের নারীমূর্তি হাতে নিয়ে সাহেব একেবারে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। আমি তখন কাগজের দপ্তর নিয়ে ব্যস্ত। কতকগুলো কাগজ ছড়িয়ে পড়েছে। দপ্তরের কাপড়গুলি সাধারণ কাপড় নয়, রেশমের ঝাড়া থেকে ‘কেটে’ তৈরি হয়—সেই কাপড়ে বাঁধা। মূল্য তার ফাইন সিল্ক থেকে কম হলেও মজবুত বেশী। তাতে লেখা রয়েছে সাল সন এবং বিষয়। আমি ওই ছড়িয়ে পড়া কাগজগুলো কুড়োতে গিয়েও একবার করে চোখ না বুলিয়ে পারি নি। যদি সূত্র পাই!
সাহেব আমাকে ডাকলেন- হ্যালো বয়!
একজন অফিসার বললেন—সাহেব ডাকছেন।
এসে দাঁড়ালাম। বলতে হ’ল—Yes sir.
সাহেব মুর্তিটা দেখতে দেখতেই বললেন—আমি শুনেছি তুমি একজন আর্টিস্ট। এবং একজন এলিট ব্যক্তি।
বললাম-আর্টিস্ট আমি বটে—ছবি আমি আঁকি কিন্তু এলিট কি না কি করে বলব?
তিনি বললেন—আমি জানি, তুমি ঠিক এই ডিস্ট্রিক্টের লোক নও। তুমি কলকাতার লোক। তোমার বাবা একজন ফেমাস জার্নালিস্ট ছিলেন, In the editorial staff of the Englishman and a regular contributor to the Statesman. তোমার একখানা চিঠি স্টেটসম্যানে বেরিয়েছিল সেও আমি জানি। I am sorry, Mr. Roy, যে তোমার ঘর আমাকে সার্চ করতে হচ্ছে! That badmash—young cousin of yours—
আমি সংশোধন করে দিলাম—No Sir, he is my uncle.
—Uncle?
—Yes sir, uncle.
—তাই। তার জন্যে তোমার ঘর সার্চ করতে হচ্ছে।
আমি নীরবে একটু হাসলাম।
এবার সাহেব বললেন—তুমি বলতে পার এ মুর্তিটি কি? অত্যন্ত সুন্দর নয়?
দেখালেন তিনি আমাকে। আমি দেখলাম। সত্যই সে মূর্তিটি অপূর্ব। সে মূর্তি আমি ছবিতে দেখেছি। প্রাচীনকালের ভাস্কর্যের নিদর্শন। খাজুরাহো মন্দিরে কোনারকের মন্দিরে এসব মূর্তি খোদাই করা আছে- মিথুন মূর্তি!
এবার আমি বাকী মূর্তিগুলির দিকে তাকিয়ে দেখলাম। দেখলাম কয়েকটাই এ মূর্তি আছে। কয়েকটা কেন—অনেকগুলো। তা ছাড়া উড়িষ্যার পত্রলেখা, প্রসাধনরতা নারীমূর্তি তাও রয়েছে। রায়বাহাদুর এগুলি সংগ্রহ করে এনেছিলেন তীর্থভ্রমণে গিয়ে। দক্ষিণের নটরাজমূর্তি, ছোট ছোট দেবমূর্তি এও রয়েছে।
আমি বললাম—আমি খুব খুশী হব ওই মূর্তিটা আপনি যদি নেন।
সাহেব বললে-না। সার্চ করতে এসে এ আমি নিতে পারি না।
অফিসারটি কাছে এসে বললেন—পরে পাঠিয়ে দেবেন। বুঝলেন!
আমি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে বললাম—তা হ’লে ওই দপ্তরগুলি কি আমি এবার গুছিয়ে নিতে পারি?
সাহেব বললেন—Oh yes, নিশ্চয় তুমি ওগুলি কুড়িয়ে গুছিয়ে তুলে নিতে পারো। তোমার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগও কিছু নেই। কিন্তু বাধ্য হয়ে এ ঘর আমাদের সার্চ করতে হল। We got information-that Atul used to keep dangerous things in the room. ওই ভাঙা জানালা দিয়ে সে এ ঘরে ঢুকত!
আমি চট করে বলে ফেললাম সুলতা তাহলে অতুলকে সঙ্গে আনলেই তো পারতেন, সে দেখিয়ে দিত কোথায় রেখেছে।
সাহেব বললেন—Oh Mr. Roy, সে পাথরের চেয়েও শক্ত। সে ভাঙে তবু কথা বলে না। বলেছে আর একজন। এবং সে সত্যি বলেছে তাতে সন্দেহ নেই। তবে পরে অতুল সরিয়ে থাকতে পারে অথবা আরও কেউ আছে যে ধরা পড়েনি, সে সরিয়ে থাকতে পারে।
একজন অফিসার এই সময় এসে স্যালুট করে দাঁড়ালেন। তাঁরা রায়বাড়ীর অন্দরমহল সার্চ করছিলেন।
সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন—Have you finished?
অফিসারটি বললেন —Yes sir, we have got the pistol.
—Pistol? You have got it?
—কোথায় পেলে?
—অতুলের সৎমা আমাদের হাতে একটা কাঠের বাক্স বের ক’রে দিয়ে বললেন—অতুল এটা তাঁকে রাখতে বলেছিল যত্ন করে, ওই মিটিংয়ের দিন দিয়েছিল, বলেছিল—পুলিশ এসে যদি ধরে তাকে, তবে তিনি যেন এটা যত্ন করে রেখে দেন, সে ফিরে এসে নেবে। কিংবা কেউ তার হাতের চিঠি নিয়ে এলে দেবে। আর পুলিশ যদি না ধরে, তবে এসেই সে নেবে। প্রথম তাঁর কোন সন্দেহ হয় নি। আজ এখন সব শুনে সন্দেহ হচ্ছে বলে তিনি বের ক’রে দিচ্ছেন। এতে কি আছে তো তিনি ঠিক জানেন না। আমরা লোহার শিক দিয়ে চাড় দিয়ে বাক্সটা খুলে দেখলাম—পিস্তল।
সাহেব হনহন ক’রে এগিয়ে গেলেন। কিছুদুর গিয়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে আমাকে ডাকলেন –Mr. Roy!
আমি তাঁর দিকে ফিরে তাকালাম।
—তোমার বাড়ীতে থাকবে তুমি। তোমার বাড়ীও আমরা সার্চ করব।
আর পায় নি কিছু ওরা সার্চ করে; ওই পিস্তলটা বের করে দিয়েছিলেন মেজঠাকুমা। ওরা সার্চ শেষ করে যাবার সময় মেজঠাকুমাকে অ্যারেস্ট ক’রে নিয়ে গেল।
আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম—মহা বিব্রত হয়ে পড়লাম। বুঝতে পারলাম না এটা কেমন ক’রে হল। মেজদি রেখেছিল অথচ আমাকে বলেনি? কার্টিজগুলোর খবর অন্যান্য জিনিসের খবর আমাকে দিলে, অথচ পিস্তলটা দিলে না, এর রহস্য আমি বুঝতে পারছিলাম না।
বুঝিয়ে দিল অৰ্চনা এসে। তার চোখ দুটো কেঁদে কেঁদে লাল হয়ে উঠেছে। আমি তখন অপরাহ্ণবেলায় চুপ ক’রে কাঁসাইয়ের ধারের জানালাটা খুলে সেইদিকে তাকিয়ে এই কথাই ভাবছিলাম। ডিক্রুজ রোজা ওই দপ্তরগুলো খাস কাছারীর উঠোন থেকে বয়ে এনে একটা ঘরে থাক্ থাক্ ক’রে রাখছিল। দু নম্বর সিন্দুকটার যাবতীয় জিনিস তাও আনছিল। রঘু খাবার করছিল। সারাদিন খাওয়া হয় নি, সে রান্নাও চড়াতে পারে নি। বিবিমহলও সার্চ করে গেছে পুলিশ সাহেব, আমার ঘরে মদের খালি বোতল এবং ভর্তি বোতলগুলি দেখে খুশীই হন নি শুধু, খানিকটা খেয়েও গেছেন, আমার আঁকা যে ছবিগুলো ছিল তারও তারিফ করেছেন। সম্ভবতঃ প্রত্যাশা করেছেন আমি ওই মূর্তি এবং একখানা ছবি এঁকে পাঠিয়ে দেব। এমন সময় অৰ্চনা এসে দাঁড়াল।
আমি শান্তভাবেই বললাম-আয়।
সে সামনেই জানালাটার একটা পাল্লা ধরে দাঁড়াল। চুপ ক’রে দাঁড়াল। হঠাৎ একসময় বললে—আমার জন্যে—। আর বলতে পারলে না, কেঁদে ফেললে সে।
আমি চমকে উঠলাম শব্দ দুটো শুনে। বললাম—তার মানে?
সে কাঁদতেই লাগল।
—অৰ্চনা!…অৰ্চনা!
এবার সে কাঁদতে কাঁদতেই মৃদুস্বরে বললে—ওটা ছোট্কা ক’দিন আগে কোত্থেকে এনে আমাকে দিয়ে বলেছিল—এটা রেখে দে। বুঝলি! হয়তো মিটিংয়ের দিন হাঙ্গামা করবে পুলিশ। যদি এস পি আসে তবে আমি ছুটে এসে নিয়ে যাব। যদি আমাকে ধরে তবে একজন কেউ এসে ঠাকুরবাড়ীতে অতিথি হয়ে থাকবে—রামকৃষ্ণ জয় রামকৃষ্ণ জয় বলে হাঁকটাক দেবে সন্ন্যাসীরা যেমন দেয়। তুই তাকে প্রণাম করবি, সে তোকে একটা শাঁখের আংটি দিয়ে বলবে, আঙুলে পরো মা সিদ্ধ হবে! তারপর তুই কোন ফাঁকে এটা দিয়ে দিবি। আমি—!
কান্নায় থামতে থামতে বলছিল সে। ছোটকা বলেছিল—খবরদার অর্চি, এটা যেন না যায়। খবরদার। তাই সব ফেলে দিয়েও ওটা আমি সেদিন ফেলি নি. তোমাদের বলি নি। আজ যখন ওরা এসে ঘিরলে আর খাস কাছারীর তালা ভেঙে ঢুকল, তখন বুঝলাম সব কেউ বলে দিয়েছে। তখন আমি মেজদিকে বললাম। ওটা আমার বাক্সের মধ্যে কাপড়ের ভিতরে ছিল। মেজদি বললে—সর্বনাশী, করেছিস কি? দে আমাকে দে, আমি যা হয় করছি। আমার হাত থেকে বাক্সটা নিয়েই মেজদি বারান্দা থেকে একজন সাবইনস্পেক্টারকে ডেকে ওই কথা বললে।
আমি বুঝলাম এবার।
মনে মনে ওই পুজুরী বামুনের যে মেয়েটি এ বাড়ীতে একান্তভাবে অন্নবস্ত্র আর মাথা গুঁজবার আশ্রয়ের জন্য পঞ্চান্ন বছরের বৃদ্ধকে বিবাহ করে দাসীপনা করেছে এককালে স্বামীর স্বামীর মৃত্যুর পর নানা গঞ্জনা মিথ্যা কলঙ্ক সহ্য করে রায়বংশধরের কাছে মাসোহারা নিয়ে এক কোণে পড়েছিল, তাকে প্রণাম করে বললাম- এ বংশে লোকে বলে ভবানী দেবী নাকি এ বাড়ীর মহীয়সী বধু, তাঁর পুণ্য তাঁর তপস্যার তুলনা মেলে না। তাঁর কথা আমি জানি না। পাই নি এখনও সব। কিন্তু তোমার তুলনা নেই তুলনা নেই তুলনা নেই!
যুবতী কুমারী অর্চনাকে বাঁচাতে আজ তুমি সব দায় নিজের ঘাড়ে নিয়ে হাতকড়া প’রে জেলখানায় গেলে।
সেদিন আমি সান্ত্বনা দিয়ে অর্চনাকে ও-বাড়ী পাঠিয়ে বলেছিলাম—আমি যা হয় করব অর্চনা—তুই ভাবিস নে!
সেদিন রাত্রিটি ঠিক আজকের এই রাত্রিটির মতই সুলতা, আমি স্থান কাল সমস্ত থেকে বিস্মৃত হয়ে ওই চিঠির দপ্তর খুলে বসেছিলাম।
বাধ্য হয়ে বসেছিলাম। কারণ এই জানবাজারের প্রকাণ্ড বাড়ীতে নিঃসঙ্গ একক হয়ে থাকতে থাকতে তোমাকে দেখে, তোমার সঙ্গে জীবন বেঁধে, পরিপূর্ণ করবার আয়োজন করতে করতে হঠাৎ সরকারী তলবে কীর্তিহাটে এসে মেজদির মধ্যে পেয়েছিলাম মাকে, পেয়েছিলাম সহোদরার মত বড়দিদিকে; বাঙলা দেশের বাঙালীঘরের ঠানদিকে। জীবনটা আমার ভরে রেখেছিলেন, আমাকে ক’রে রেখেছিলেন একটি নাবালক কিশোর বালক। আমি সমাদরের লোভে তাই হয়ে উঠেছিলাম। কীর্তিহাটের সবই আমার কাছে ছিল অরুচির বস্তু। কিন্তু তিনিই ছিলেন আমার রুচি—কীর্তিহাটের স্বাদ।
১৯৩৬ সাল, মেদিনীপুর জেলা, পর পর তিন তিন জন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট খুন হয়েছে, ১৯২১ সাল থেকে এ পর্যন্ত গোটা জেলাটায় কীর্তিহাটে রায়দের প্রভাবে গড়া ইউনিয়ন বোর্ড ছাড়া অধিকাংশ জায়গাতে ইউনিয়ন বোর্ড হয় নি, হলেও ট্যাক্স আদায় হয় নি। দেশপ্রাণ বীরেন্দ্র শাসমলের সে যুদ্ধের আগুন এখনও জ্বলছে, মেদিনীপুর ক্ষুদিরামের জন্মভূমি; সারা জেলাটায় ইংরেজ পুলিশ দিয়ে কিছু করতে না পেরে গাড়োয়ালী পল্টন এনে জেলা শাসন করছে। ১৯৩৪ সালে ব্রজকিশোর, রামকৃষ্ণ, নির্মলজীবনের ফাঁসি হয়ে গেছে।
অর্চনা বলে গেল—অতুল বলেছিল—কেউ আসবে রামকৃষ্ণ জয় রামকৃষ্ণ জয় ব’লে। তার হাতে পিস্তলের বাক্স যেন সে দেয়।
রামকৃষ্ণদের সঙ্গে অতুলের সংযোগ রয়েছে। সুতরাং কত বড় এবং জটিল মামলা পুলিশ গড়তে পারবে, সে পুলিশ জানে, কিন্তু পিস্তলটা যখন মেজদিদি নিজে বের ক’রে দিয়েছে তখন অন্ততঃ তাঁকে আর্মস অ্যাটে সাজা না দিয়ে ছাড়বে না!
এর প্রতিকার মামলা। কিন্তু মামলা করেও তো ফল হবে না। উদ্বেগ এবং উৎকণ্ঠার আমার শেষ ছিল না। কোন দিকে এক বিন্দু আলো আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না। তাই অন্যমনস্ক হবার জন্যই ওই পুরনো চিঠির দপ্তর নিয়ে বসেছিলাম।
চিঠির পর চিঠি; সে দপ্তরটার সবই ম্যাজিস্ট্রেট, এস পি, এস ডি ও সাহেবদের চিঠি। বীরেশ্বর রায়ের লেখা চিঠির নকলও কিছু কিছু ছিল। সব চিঠিই ইংরেজের জয়গানে মুখরিত। সেটা ভাল লাগে নি।
অন্য একটা খুলে ছিলাম। কাপড়ে সাল সন দেখেই খুলেছিলাম। সে ১৮৫৭ সাল। তার মধ্যে প্রথমেই পেয়েছিলাম মেদিনীপুর জেলা ইস্কুলের হেডমাস্টার বাংলাদেশের বিখ্যাত রাজনারায়ণ বসুর পত্র।
সত্যেন বোস, কানাইলালের সঙ্গে শত্রুতায় নরেন গোসাঁইকে মেরে ফাঁসি গিয়েছিলেন—রাজনারায়ণ বোস সত্যেন বোসের পিতামহ। অরবিন্দ ঘোষ বারীন ঘোষের মাতামহ। তাঁকে পত্র লিখেছিলেন বীরেশ্বর রায়, কি লিখেছিলেন তার নকল নেই, তবে তিনি যে কলকাতার অবস্থা লিখেছিলেন তার উল্লেখ ছিল চিঠিতে—
“আপনার পত্রে কলিকাতার বর্তমান অবস্থার কথা সম্যক অবগত হইলাম এবং যুগপৎ ভীত হইলাম ও দুঃখ অনুভব করিলাম। আপনি কলিকাতায় ইংরাজদিগের উদ্বেগ এবং গবর্নর জেনারেল লর্ড ক্যানিং মহোদয়কে এদেশের সমুদয় লোকের উপর উত্তেজিত করিবার প্রয়াসের কথা লিখিয়াছেন, তাহাতে উদ্বেগ বৃদ্ধি পাইল। আবার অযোধ্যার নবাব সাহেব ওয়াজিদ আলি শাকে কেল্লার মধ্যে বন্দী করিবার সময় তিনি যে গলদশ্রু হইয়া বিলাপ করিয়াছেন, তাহাতে কে দুঃখিত না হইয়া থাকিতে পারে। এবং গবর্নর জেনারেল বাহাদুর লর্ড ক্যানিংকে নমস্কার জানাই। ক্লেমেন্সি ক্যানিং তাঁহার সার্থক নাম। কোনরূপেই বুঝিতে পারিতেছি না মঙ্গল কিসে? ইংরাজের সভ্যতায় আমাদের এই নবজাগরণের সময় ইহার বিপর্যয় ঘটিলে আবার আমরা অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত হইব। ইহা নিশ্চিত।
তবে অত্র জেলায় অবস্থাও আদৌ শান্তিপূর্ণ নহে। বড়ই ভীতির মধ্যে বসবাস করিতেছি। এখানেও সিপাহী বিদ্রোহের ভারতব্যাপী তরঙ্গ আসিয়া পৌঁছিয়াছে। মে মাসে একজন তেওয়ারী ব্রাহ্মণ সিপাহী আসিয়া অত্রস্থ রাজপুত জাতীয় সিপাহীর পল্টনকে বিগড়াইবার চেষ্টা করে। কর্নেল ফস্টর উক্ত পল্টনের অধিনায়ক, তিনি তেওয়ারীকে ফাঁসি দিয়াছেন। এবং পল্টনের সিপাহীদিগকে ধানদূর্বা লইয়া বিশ্বস্ত থাকিবার শপথ লওয়াইয়াছেন। ফস্টর সাহেবের একজন রাজপুত রমণী রক্ষিতা আছে। উক্ত রমণী অশ্বপৃষ্ঠে ফস্টর সাহেবের সঙ্গে ঘুরিতেছে এবং পল্টনের সিপাহীদিগকে বুঝাইতেছে।
তথাপি আশঙ্কার শেষ নাই। সাহেবগণ কাঁসাই নদীতে নৌকা প্রস্তুত রাখিয়াছে। প্রয়োজন হইলে স্ত্রীপুত্রদের চাপাইয়া ইংলণ্ড অভিমুখে রওনা করিয়া দিবে। হিজলীর মুখে জাহাজে চড়িবে। আমরাও খুব ভীত ভাবে দিনাতিপাত করিতেছি। ইস্কুলে পেন্টালুনের ভিতর ধুতি পরিয়া থাকি। যখনই সিপাহী আসিবে তখনই পেন্টালুনের চাপকান ছাড়িয়া ধুতি ও চাদর বাহির করিয়া ফেলিব। সিপাহীদিগের পেন্টালুনের উপর খুব রাগ
এখানকার অবস্থা সমুদয় জ্ঞাত করিলাম। কলিকাতার অবস্থার সঙ্গে তুলনীয় না হইলেও ভয় রহিয়াছে। তবে কলিকাতা হইতে চলিয়া আসিয়া ভালই করিয়াছেন। এবং এখন হইতে এখানে থাকিবার সংকল্প করিলে আরও সুখী হইব। মহাশয়ের সহিত পরিচয় না থাকিলেও আপনার নাম শুনিয়াছি। একটি মধ্য ইংরাজী ইস্কুল স্থাপনের কথা পুর্বে শুনিয়াছিলাম কিন্তু মহাশয়ের পত্নী বন্যার জলে ভাসিয়া যাওয়ায় নিরতিশয় দুঃখে এখান হইতে কলিকাতায় গিয়াছিলেন বলিয়া তাহা কার্যে পরিণত হয় নাই। এখন যখন ফিরিয়া আসিয়াছেন তখন এই সকল জাতীয় কল্যাণমূলক কার্যগুলি সম্পাদনকরতঃ মনুষ্যজীবন সফল সার্থক করুন।” *
[*পত্রখানির মর্ম রাজনারায়ণ বসুর জীবনী হ’তে গৃহীত। কিছু কিছু মেদিনীপুরের ইতিহাসের ঘটনার কথা এর মধ্যে দেওয়া হয়েছে। যেমন—কর্নেল ফস্টরের রাজপুত প্রণয়িনীর কথা।]
চিঠিপত্র নিয়েই সেদিন ও সারারাত্রি আমার কেটে গিয়েছিল সুলতা। মধ্যে মধ্যে ঢুলেছি। কিছুক্ষণ ঘুমিয়েছি। আবার জেগেছি আবার পড়েছি। এমনিভাবেই তখন ভোর হচ্ছে, এমন সময় ঘোষ নায়েব, যাকে মেদিনীপুর পাঠিয়েছিলাম অতুলেশ্বরের জামিনের জন্যে, সে ফিরে এল উকীলের চিঠি নিয়ে
ভাল উকীল তিনি। নতুন উঠছেন। তিনি পত্র লিখেছেন, চেষ্টা তিনি করছেন। কিন্তু বর্তমান অবস্থা খুবই প্রতিকূল। তবে শোনা যাচ্ছে বৃদ্ধ রিটায়ার্ড আই-সি-এস গ্রিফিথ সাহেব চলে যাচ্ছেন। আসছেন বাঙালী আই-সি-এস-বি আর সেন। সেন সাহেবের সুশাসক বলে সুনাম আছে। এবং জোর গুজব এবার গভর্নমেন্ট এত কড়াকড়ির পর একটা আপোস করবার চেষ্টা করবেন লোকদের সঙ্গে। তার আর বিলম্ব নাই। সপ্তাহখানেকের মধ্যেই সেন-সাহেব চার্জ নেবেন। এবং কড়াকড়ি অনেক শিথিল হবে। বর্তমান কেসের অবস্থা এমন গুরুতর নয়। মাত্র ১৪৪ ধারা ভঙ্গ। তবে গোপনে জানলাম রামকৃষ্ণ, যার ফাঁসি হয়েছে, তার দলের সঙ্গে যুক্ত করবার চেষ্টা করছে। তা হ’লেও সেনসাহেব এলে সাধারণ ভাবেই বিচার হবে। তাতে ছ’মাস পর্যন্ত জেল হতে পারে। তার বেশী নয়।
তখনও মেজদি হাতকড়া প’রে মেদিনীপুরে উপস্থিত হন নি।
আমি ভাবছিলাম-আমি গিয়ে সেন-সাহেবের কাছে হাতজোড় করে বলব, এ মহিলাটি একান্তভাবে নির্দোষ। এঁকে দয়া করে ছেড়ে দিন। সন্তানবাৎসল্যের পুণ্যের উপর এমন নিষ্ঠুর আঘাত হানবেন না।
এক সপ্তাহের মধ্যে সেনসাহেবও এলেন, আমিও গেলাম, পুলিশসাহেবকে সেই মূর্তিটা শুধু নয় আরও দু তিনটে ওই ধরনের মূর্তি এবং আমার আঁকা ছবিও দিয়ে দেখা করে এলাম। নিবেদন জানিয়েও এলাম।
সেটেলমেন্ট তখন বন্ধ হয়েছে কয়েক মাসের জন্য। কিন্তু মেজদির জন্যে কলকাতায় ফিরে আসা আমার হল না। আমার অবলম্বন হল ওই দপ্তর।
প্রায় আশী বছর সুলতা, ১৯৩৬ সাল থেকে ১৮৫৭, আশী বছরের এক বছর কম হবে, ঊনআশী বছর, সাতান্ন সাল আর ৩৬ সালের মাস কয়েকটা যোগ দিলে পূর্ণ আশী বছর। এই আশী বছর পূর্বের বাংলাদেশের মধ্যে বিচরণ করে এ কালকে ভুলে রইলাম। মনে রইল শুধু দুটি একালের মুখ। একটি মেজদির, অন্যটি তোমার। তবে মেজদির চেয়ে তুমি ম্লান হয়ে গিয়েছিলে এ সত্য আমি স্বীকার করব। একটা রক্তমাখা মসলিনের যবনিকা তোমাকে আড়াল ক’রে দাঁড়িয়েছিল।
এরই মধ্যে একে একে আবিষ্কার করলাম সব। পেলাম সব।
সুরেশ্বর বললে—চার মাস ধরে এই চিঠিপত্রগুলি সব পড়েছিলাম সুলতা। প্রথম প্রথম বেছে বেছে পড়েছিলাম, তারপর নির্বিচারে সব।
প্রথম বেছে বেছে পড়েছিলাম মানে, চিঠির কিছুটা পড়ে আমি খুঁজছিলাম, রায়বাড়ীর যে সত্যকে রত্নেশ্বর রায় ভয় পেয়ে নিজের ডায়রীতে লেখেন নি। বীরেশ্বর রায় লিখতেন, তিনি সব দোষ সত্ত্বেও নির্ভীক পুরুষ ছিলেন, সত্যকে তিনি না-লেখা হতেন না। এ সত্য তাঁর সময়ে তাঁর সম্মুখেই আবিষ্কৃত হয়েছিল। কিন্তু স্মরণীয় ঘটনার খাতা লেখা তিনি বন্ধ করেছিলেন। সে সত্য তাঁরা যেভাবে দেখেছিলেন, তা বড় ভয়ঙ্কর সুলতা। পড়ে আমিও ভয় পেয়েছিলাম। মনে মনে বার বার কুসংস্কার বলে উড়িয়ে দিতে চেয়েও পারি নি। কিন্তু সত্যটুকু আবিষ্কার করতে গিয়ে নূতন সত্য আবিষ্কার করলাম। সেই ঘটনাটাই আগে বলি, তখনও পর্যন্ত যে কথা গোপন করে গেছেন রত্নেশ্বর রায়, যা লিখে যান নি বীরেশ্বর রায়, তা আমি পাই নি। কিন্তু নতুন যেটা পেলাম, তা বিস্ময়কর।
মেজদি আর অতুলের মামলাটা হঠাৎ মাঝখানে ঘোরালো হয়ে উঠল। আমাদের কীর্তিহাটের পাশের গ্রামের হরি সিং দফাদার মাঝখানে তার নিজের ষোল বছরের ছেলেকে পুলিশের কাছে হাজির করলে। ছেলেটার নাম শিবু। কীর্তিহাটের স্কুলে পড়ত। অতুল কীর্তিহাটের স্কুল থেকে ছেলে সংগ্রহ করত। ছেলেটার কাছ থেকে হরি সিং নিজেই বের করেছিল একখানা ছোরা, কতকগুলো ইস্তাহার, আর খানকয়েক চিঠি। অতুলের লেখা চিঠি। অতুল মেজদি অ্যারেস্ট হবার মাসখানেক পর, তখন আমি মেদিনীপুর শহরে একটা বাসা নিয়েছি, মধ্যে মধ্যে যাই, থাকি। মামলার তদ্বির করি। আশা হচ্ছিল, অন্তত উকীল বলছিলেন সম্ভবতঃ মেজদির জামিন হবে, এবং তিনি খালাস পেয়ে যাবেন। কারণ তিনি তো ঠিক জানতেন না যে, ওই বাক্সটার মধ্যে পিস্তল আছে।
হঠাৎ সেদিন গিয়ে শুনলাম, হরি সিংয়ের ছেলে অ্যারেস্ট হয়ে, জট পাকিয়ে, মামলা ঘোরালো হয়ে উঠেছে। ছেলেটা স্টেটমেন্ট দিয়েছে যে, অতুলবাবুর দলের ছেলে সে। পুলিশ, ইংরেজ এদের মারবার জন্যে খুব বড় দল আছে, তার নাম সে জানে না। সে অতুলবাবুকে লীডার জানে, আর কয়েকজনকে জানে। এ ছোরা, ইস্তাহার সে অতুলবাবুর কাছে পেয়েছে। তিনি রাখতে দিয়েছিলেন। অতুলবাবুর কাছে পিস্তল, গুলী আছে। সে দেখেছে। ক’ বছর আগে মেদিনীপুর সদরঘাটে কাঁথির এস-ডি-ও আর পুলিশসাহেব সামসুদ দোহাকে গুলী করে মারবার কথা যখন হয়েছিল, তখন সে অতুলবাবুর সঙ্গে মেদিনীপুরের সদরঘাট পর্যন্ত গিয়েছিল। কিন্তু এমন পুলিশ ছিল চারদিকে যে, কেউ কাছে যেতে পারে নি। মেদিনীপুরের দুজন বড় নেতা ছিল। তাঁদের নাম সে জানে না। তারা ফিরে এসেছিল। অতুলবাবু শঙ্কর সেন আর দোহাসাহেবকে মারতে পারেন নি বলে রাস্তায় কেঁদেছিলেন। কীর্তিহাটে ফিরে অতুলবাবুর বাড়ীতে জল খেয়ে সে বাড়ী গিয়েছিল। অতুলবাবুর মা জল খেতে দিয়েছিলেন। অতুলবাবুকে বলেছিলেন—আমার ভাগ্যি যে ফিরেছিস। তুই ফিরবি, এ আশা আমি রাখি নি। এর পর পুলিশ ভাবছে, শুধু আর্মস অ্যাক্টে কেস করবে, না কন্সপিরেসি কেস করবে।
পুলিশের আপত্তিতে মেজদির সঙ্গে ইন্টারভ্যু পর্যন্ত পাই নি সেদিন। কীর্তিহাটে ফিরে এলে—তখন এই মামলার সময় ধনেশ্বর কাকা আসতেন, কল্যাণেশ্বর আসত, বিমলেশ্বর কাকা আসতেন, খোঁজ নিতেন মামলায় কি হল? প্রণবেশ্বরদা পালিয়ে এসেছিলেন কলকাতায়, পাছে এর সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন বলে।
হরি সিংয়ের ছেলে শিবু সিং ধরা পড়ে কেস জটিল হয়েছে শুনে ধনেশ্বর কাকা বলে- ছিলেন-নারায়ণ, নারায়ণ! হরি সিংয়ের ছেলে? সর্বনাশ, সর্বনাশ!
তারপর তাঁর অভ্যস্ত অ্যাক্টিংয়ের ভঙ্গিতে বলে উঠেছিলেন-এ মিথ্যা, এ মিথ্যা, এ মিথ্যা! কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে থেকে বলে উঠেছিলেন-বা-রে অদৃষ্ট বা! বা-রে তোর রচনা করা জাল! যখন বিপক্ষে তুই যাস, তখন লোহার বাসরঘরে সুচীছিদ্রে ঢোকে কালনাগিনী। বেহুলার পায় কালঘুম। মতিভ্রম ঘটাস তুই!
কথাটা বুঝতে পারি নি। তারপর পরিষ্কার হয়েছিল। কল্যাণেশ্বর জিজ্ঞাসা করেছিল—হরি সিংহের পূর্বপুরুষের সঙ্গে কি একটা ঘটেছিল না জ্যাঠামশায়?
ধনেশ্বর কাকা বলে উঠেছিলেন—গোপাল সিং, দুর্ধর্ষ গোপাল সিং। মহিষাদলের মণ্ডলান মৌজা বীরপুর বীরেশ্বর রায় বন্দোবস্ত নিয়েছিলেন, গোপাল সিংকে শাস্তি দিতে। দিয়েছিলেন বীরেশ্বর রায়। মামলায় মামলায় সর্বস্বান্ত করেই ক্ষান্ত হন নি, মৌজা বীরপুরের মণ্ডলী কেড়ে নিয়ে সকলের সমক্ষে কাছারীর মেঝের উপর খড় ফেলে দিয়ে বলেছিলেন, দাঁত দিয়ে ওঠাও তারপর নিজের চোখের সামনে রাখবার জন্য তাকে এনে বাস করিয়েছিলেন পাশের গ্রামে। জমি-জেরাত দিয়েছিলেন। ঘর করবার টাকা দিয়েছিলেন। সবই দিয়েছিলেন। হুকুম ছিল, রোজ সকালে এসে সেলাম দিয়ে যাবে। তার জন্য একটা বার্ষিক বৃত্তি ছিল তার। সর্দারী বৃত্তি—গোপাল সিং। বন্ধ করেছিলেন আমার বাবা।
কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক হল তাঁর, অথবা করুণ হল, বললেন—তখন বাবার অবস্থা হীন হয়েছে। যোগেশ্বরদা যজ্ঞেশ্বরদা সেখানকার ঐশ্বর্যে মত্ত। কীর্তিহাটের মায়া-মমতা নেই। সেবার থিয়েটার হচ্ছে আমাদের, ওই হরি সিং-এর বাপ তখন বুড়ো, হরি সিংয়ের বয়স আঠারো-উনিশ। হরি সিংয়ের রাম সিংয়ের কথা ছিল, ঘুরে ঘুরে গোলমাল থামাবার। বুড়ো তা না করে ইস্কুলের বেঞ্চে বসে তামাক খাচ্ছিল। প্রফুল্ল প্লে। বাবা নিজে যোগেশ। আমি নব-যুবক। আমি সেবার প্রথম নামব। আমি শিবনাথ। বাবা গ্রীনরুমের দরজায় দাঁড়িয়ে হাঁকলেন, রাম সিংকে ডাক তো রে, বেঞ্চিতে বসে আছে। তিনি যে কি করে তার ভদ্রলোকদের সঙ্গে বেঞ্চে বসে হুঁকোয় তামাক খাওয়া দেখেছিলেন, তিনিই জানেন। আমাদের চাপরাসী যোগীন্দর পাঁড়ে ডাকতে গিয়ে ফিরে এসে বললে-সে বললে—এখন উঠলে তার জায়গা যাবে। পরে দেখা করবে। তা সে রাত্রে তো এলই না। পরে একদিন এলে বাবা বললেন—রাম সিং, তোমরা একটা বৃত্তি পাও আমাদের কাছে, খাতাতে লেখা আছে, সর্দারী বৃত্তি মাসিক এক টাকা হিসাবে বারো টাকা। নিচে দাগ দিয়ে লেখা আছে, নিত্য কাছারীতে হাজিরা দিবার জন্য এবং ক্রিয়াকর্মে-পার্বণে সর্দারী কাম নির্বাহের জন্য! ও বৃত্তি আমি বন্ধ করলাম। বুঝেছ! বেঞ্চিতে বসে হুঁকো টেনে সর্দারী করা হয় না!
রাম সিং চুপ করে ছিল, এই হরি সিং সঙ্গে ছিল, সে বলেছিল-সে সব দিন চলে গিয়েছে বাবু। মাসে এক টাকায় এখন গরুর রাখাল মেলে না। আর বৃত্তি? সে না পাই তো দেখা যাবে আদালতে। আদালতও করেছিল, কিন্তু তাতে হেরেছিল। খাতার লেখার নমুদ আদালত ফেলতে পারে নি। আমার মনে পড়ল। সেদিন পর্যন্ত ফাইলে চিঠিপত্রের মধ্যে দিয়ে যে পর্যন্ত এসেছি, তাতে মিউটিনির সময় বীরেশ্বর রায় কীর্তিহাটে এসে পাকা হয়ে বসেছেন। নতুন পত্তনী নেওয়া জমিদারীর খাজনা বৃদ্ধি করছেন। বীরপুরে মামলা শুরু হয়েছে, গোপাল সিংয়ের সঙ্গে, মণ্ডলান মহলের মণ্ডলান প্রথা তুলে দেবার জন্য।
কথাটা আমি ঠিক বিশ্বাস করি নি, সুলতা। মেদিনীপুর থেকে বাড়ী আসার পথশ্রম সত্ত্বেও অর্ধেক রাত জেগে ওই কথাটা ভেবেছিলাম, আর মধ্যে মধ্যে এক-একখানা চিঠি তুলে নিয়ে পড়ছিলাম।
পরের দিন সকালে বৃদ্ধ রঙলাল মণ্ডল মশায় এসেছিলেন। ওই কথাটা শুনেই এসেছিলেন। আর এসেছিলেন দয়াল ঠাকুরদা। দুজনেই ধনেশ্বর কাকার কথারই প্রতিধ্বনি করে বলে- ছিলেন—এ হে-হে, অতুলবাবু সিংদের বাড়ীর ছেলেকে বিশ্বাস করলেন কেন গো। ছি-ছি-ছি। এ অন্যায় হয়েছে।
দয়াল ঠাকুরদা বলেছিলেন—অতুল এ সব জানত না নাকি? দূর-দূর-দূর! এ কি করলে সে?
স্কুলের হেডমাস্টারও সেদিন এসেছিলেন। তিনিই কেবল বলেছিলেন—হরি সিং অবশ্য করে থাকতে পারে, আক্রোশবশে। গল্পটা প্রবীণেরা জানে। রাম সিংয়ের ব্যাপার আমার আমলেই। কিন্তু. শিবু এমন তো করতে পারে না। ছেলেটা ক্লাসে থার্ড-ফোর্থ হয়। ভাল ছেলে! অনেস্ট ছেলে!
সবই সত্যি সুলতা। গল্প, রচনা করা গল্প নয়, বাস্তব জীবনের প্রত্যক্ষ ঘটনা। শিবুও সত্যিই ভাল ছেলে। পরে সে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় স্কলারশিপ পেয়েছে। দুই-ই সত্যি এবং তার সঙ্গে এটাও সত্যি যে, শিবু এই সব ঘটনার কথা সারারাত্রি ধরে বাপের কাছে শুনে তারপর পুলিশের কাছে স্টেটমেন্ট দিয়েছিল।
বাপ তার একদিন হঠাৎ ওই ছোরা আর চিঠি আবিষ্কার করার পর ছেলেকে ওইভাবে সারারাত বলে বলে তাকে উত্তেজিত করে স্বীকার করিয়েছিল।
আদালতের জেরাতে সে তা স্বীকার করেছিল।
কন্সপিরেসি কেস পুলিশ করতে পারে নি। মেদিনীপুর মেদিনীপুর। এর জোড়া বাংলাতে নেই, বোধ করি ভারতবর্ষেও নেই। সেখানে কন্সপিরেসি কেস করে সাক্ষী পাওয়া যায় না।
ম্যাজিস্ট্রেট ‘পেডি’ মার্ডার কেসে বিমল দাসগুপ্তকে ফাঁসি দেবার জন্যে হাইকোর্টে স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল বসিয়েছিল। কিন্তু কলেজিয়েট স্কুলের হেডমাস্টার হীরালালবাবু আর নারায়ণবাবুকে পুলিশ সেই দারুণ নির্যাতনের সময় ভয় দেখিয়েও সাক্ষী দেওয়াতে পারে নি। স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল অ্যাডভোকেট জেনারেল উঠিয়ে নিয়েছিলেন। সাক্ষী অতুল মেজদির কেসেও মেলে নি। শুধু শিবু অ্যাপ্রুভার হয়েছিল। আমাদের উকীল ওই জেরাই করেছিলেন।
—গোপাল সিংয়ের নাম শুনেছ? তোমাদের পূর্বপুরুষ?
শিবু বলেছিল—হ্যাঁ জানি।
—তুমি শুনেছ, তাঁকে বীরেশ্বর রায় জমিদার সর্বস্বান্ত করেছিলেন মামলা করে, দাঁতে কুটো করিয়েছিলেন—
সরকারী উকীল আপত্তি করতে ছেলেটি বলে উঠেছিল—হ্যাঁ জানি।
—কি করে জানলে? কে বললে?
—বাবা।
—কবে বললে, যেদিন পুলিশের কাছে স্টেটমেন্ট দাও, তার আগের দিন? না অনেক আগে?
—না, সেই দিন রাত্রে। কিছুটা কিছুটা জানতাম আগে থেকে।
আদালতে আমি ছিলাম, আমি সব ভুলে গিয়ে শুধু ভেবেছিলাম কি জান? ভেবেছিলাম—নাঃ, সুলতার কাছে ফিরে গিয়ে কাজ নেই। যদি যাই তবে রত্নেশ্বর রায় আর ঠাকুরদাস পালের ঘটনাটা চিরদিন বিষাক্ত লোহার শলার মতো আমাদের দুজনের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকবে। না, কাজ নেই, কাজ নেই।
শুধু অতুল চুপ করে ছিল।
আর মেজদি বলেছিলেন—তা বেশ হল। দেনা শোধ হল! হেসেছিলেন।
অতুল এবং মেজদির জেল হয়ে গেল। অতুলের দু বছর, মেজদির ন মাস। মেজদিকে খালাস করবার জন্যে চেষ্টার আর বাকী রাখি নি, কলকাতা থেকে ব্যারিস্টার নিয়ে গিয়ে- ছিলাম। তিনি ওইটের উপরেই জোর দিয়েছিলেন; মেজদি নিতান্ত সরল, সেকেলে ধরনের বড়ঘরের বউ; এক বৃদ্ধ ধনী তাঁকে তৃতীয় পক্ষে বিয়ে করেছিলেন; অতুল তাঁর স্বামীর ছোট ছেলে, সতীন-পুত্র। তিনি এসে এই ছেলেটিকে মানুষ করে মায়ের চেয়েও মায়ায় জড়িয়ে পড়েছিলেন। এদেশের অল্পবয়সে বিধবারা যেমন ধর্মকর্ম নিয়ে থাকেন, বাইরের জগতের সঙ্গে সংস্রব চুকিয়ে দিয়ে, ইনিও ঠিক তাই। এবং তার উপর নিতান্ত সরল মানুষ। দেশ স্বাধীন বা পরাধীন, এতে তাঁর কিছু যায় আসে না। অতুল ওই মিটিংয়ের দিন যাবার সময় পিস্তল-ভরা বাক্সটা তাঁর কাছে রাখতে দিয়েছিল। বলেছিল, এটা রেখে দিও। উনি রেখে দিয়েছিলেন, জানতেনও না কি রেখেছে এর মধ্যে। পুলিশ সার্চ করতে আসবামাত্র বের করে দিয়েছেন। পিস্তল যে বাক্সে ছিল, সেটা এই বিখ্যাত জমিদারবাড়ির আগের কালের একটা আইভরির কাজ-করা চন্দন কাঠের বাক্স, সেটা চাবিবন্ধ ছিল। চাবি তাঁর কাছে ছিল না। কাজেই এ যে তিনি জানতেন না, এটা নিশ্চিত। সুতরাং এতে যদি তাঁর শাস্তি হয়, তবে একান্তভাবে নির্দোষ একটি নারীকে, নারীজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ হৃদয়সম্পদ মাতৃস্নেহের জন্য শাস্তি পেতে হবে। সম্ভবতঃ ঈশ্বর লজ্জিত হবেন। হয়তো বা ক্রাইস্ট দ্বিতীয়বার ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার যন্ত্রণা ভোগ করবেন এবং ঈশ্বরকে ক্ষমা করবার জন্য প্রার্থনা জানাতে তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যাবে।
সকলেই অভিভূত হয়েছিল। কিন্তু বিচারক হন নি, হতে পারেন নি। ট্রাইব্যুনাল নয়, সেসন নয়, ম্যাজিস্ট্রেট বিচারকের আদালতে বিচার; তিনি তাঁকে ন মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়ে লিখেছিলেন—লার্নেড ব্যারিস্টার যে বলেছেন, তিনি এসব বুঝতেনই না, তা আমি বিশ্বাস করতে পারি না। এই জেলাটি মেদিনীপুর, এখানকার সাধারণ মানুষ পর্যন্ত এই ধরনের অন্যায় অপরাধকে সর্বাপেক্ষা মহৎ কর্ম মনে করে। শুনেছি, ছেলের ফাঁসি হলে সে ছেলের মা ছেলের জন্য গৌরব অনুভব করে। তার উপর দিস ফ্যামিলি ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে শিক্ষিত জমিদার বংশ। পাবলিক প্রসিকিউটর তার একটি চিত্র তুলে ধরেছেন। এই বংশে একজন বীরেশ্বর রায় ছিলেন, তিনি বাড়িতে ইংরেজ ধর্মপ্রচারক মিঃ হিলের কাছে ইংরাজী শিখেছিলেন। মিউটিনির সময় এই জেলার বিদগ্ধ হেডমাস্টার রাজনারায়ণ বোস এবং অন্যদের সঙ্গে দুর্ধর্ষ দুষ্ট প্রকৃতির সিপাহীদের চেয়ে ইংরেজ শাসন মঙ্গলজনক তা বুঝতেন, এবং বুঝে সহযোগিতা করেছিলেন। বীরেশ্বর রায়ের ছেলে রত্নেশ্বর রায়বাহাদুর এবং শিক্ষিত লোক ছিলেন। সেই বংশের কোন বধূ যে এতখানি নির্বোধ হতে পারে তা মনে করি না। এবং অ্যাপ্রুভার শিবচন্দ্র সিং বলেছে, কন্টাইয়ের এস-ডি-ও এবং এস-ডি-পি-ও শঙ্কর সেন এবং সামসুদ দোহাকে, যারা সরকারী কাজ দৃঢ়তার সঙ্গে করত, তাদের মারবার জন্য এসে ব্যর্থ হয়ে যেদিন ফিরে যায়, সেদিন দিস লেডি তাদের যত্ন করে খাইয়েছিলেন, উৎসাহজনক বাক্য বলেছিলেন। এ কথা আমি বিশ্বাস করি। সুতরাং তাঁকে নির্দোষ আমি মনে করতে পারি না। সুতরাং—।
একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সুরেশ্বর বললে—জেল হয়ে গেল।
দু দিন পর অনেক চেষ্টা করে ইন্টারভ্যু পেলাম। এ পর্যন্ত আণ্ডার ট্রায়াল অবস্থায় কোন রকমেই ইন্টারভ্যু পাই নি। বিচারের পর পেলাম।
অতুলকে বললাম—তুমি কি শিবুদের ব্যাপার জানতে না?
সে হাসলে। চুপ করে রইল। বললে-অন্য কথা বল। ওর জন্যে আপসোস করে কি হবে?
তারপর বললে—দেখ, একটা অনুরোধ করব, তোমার অনেক টাকা আছে, একটি ভাল পাত্র দেখে অর্চির বিয়েটা দিয়ে দিও।
বললাম-বিয়ে করবে সে? আমি জানি না।
অতুল বললে-বলো আমার নাম করে। মেজদাকে তো জান—।
বললাম- আমি তা করব।
মেজদির সঙ্গে ইন্টারভ্যু পেয়েছিলাম ওই দিন। বললাম- মেজদিকে কি বলব?
অতুল বললে—প্রণাম দিও। বলো, আমি বুঝেছি সব।
জেলের অফিসার বললে-সময় হয়ে গেছে।
হেসে অতুল চলে গেল।
অতুল বুঝেছিল, মেজদি অর্চনাকে বাঁচাবার জন্যই দায়টা নিজে নিয়ে পিস্তলটা বের করে দিয়েছেন। সেটাই সে ইঙ্গিতে বলে গেল।
আধ ঘণ্টা পর মেজদির সঙ্গে ইন্টারভ্যু।
মেজদি আমাকে দেখে একমুখ হেসে বলেছিলেন—এসেছিস!
—হ্যাঁ।
—আমাকে রক্ষে করবার জন্যে এত টাকা খরচ করলি ভাই? অবিশ্যি তোর আছে, খরচ করেছিস, আমি বলবার কে? তা বেশই করেছিস। এখন একটা কাজ করিস ভাই, তোর সাত পুরুষ তোকে আশীর্বাদ করবেন। অর্চির একটা গতি করে দিস। ওরে, তুই হয়তো বিশ্বাস করবি নে। তোরা হালআমলের ইংরেজী জানা আধা-সাহেব, ওরে ও হল সেই আমার বড় শাশুড়ী। তোর ঠাকুরদা আমাকে স্বপ্নে বলে গেছেন। বংশকে রক্ষে করতে এসেছেন!
আমি কথা বলতে পারি নি। গলাটা যেন কান্নায় বুজে আসছিল।
মেজদি তাঁর বড় বড় চোখ দুটি আরও বড় করে বললেন—জানিস, জেলখানায় এসে নানান জাতের মেয়ের মধ্যে জাত-ধর্ম কি করে বাঁচাব, কি করব, এই ভেবে প্রথম দু-তিন দিন খুব কাঁদতাম, আর আপসোস করতাম, গোবিন্দকে ডেকে বলতাম—শেষে এই করলে ঠাকুর? ভাই, তিন দিনের দিন শেষরাত্রে ঘুমটি এসেছে, আর তোর মেজঠাকুরদা এসে শিয়রে দাঁড়ালেন। আমি শিউরে উঠলাম। তিনি হেসে বললেন—“ভয় লাগছে নাকি ছুটকী?’ আমি বললাম—’না’। তিনি বললেন—তবে শিউরে উঠলে কেন গো?’ বললাম—’এ পাপপুরীতে কেন এলে তুমি, কেন এলে? বের হবে কি করে?’ তা বললেন—’আমরা তো এখন শূন্যে শূন্যে যাই, আমাদের কি জেলখানায় আটকাতে পারে? এই বুদ্ধি হল শেষে! আর এসেছি তোমাকে আশীর্বাদ করতে গো। তুমি অর্চিকে রক্ষা করেছ। অর্চি কে জান? উনি হলেন সেই ঠাকুমা। তপস্বিনী বউ রায়বাড়ীর। আর অতুল হল আমার বাবা। রায়বাহাদুর। আর সুরেশ্বর আমার দাদা। ওরা সব ঋণ শোধ করতে এসেছে। দেখনি, অর্চনার সঙ্গে ঠাকুমার মিল। আর সুরেশ্বরের সঙ্গে আমার দাদার চেহারার মিল! তুমি অর্চিকে শুধু বাঁচাও নি। ওই গোপাল সিংদের ওপর অত্যাচারের মাত্রা বেশী হয়েছিল, সেটাও শোধ হল। বুঝেছ?’
আমি চুপ করে শুনেই যাচ্ছিলাম। প্রতিবাদ করিনি। এতটুকু অবিশ্বাসের ছায়া কি ছাপ আমার মুখে পড়েনি। আমার বুকের ভিতরটা একটা আবেগে ভরপুর হয়ে উঠেছিল। ভাববার ও ক্ষমতা ছিল না যে, এই সরল প্রাচীন আমলের বিশ্বাসী-মন মেয়েটি আপনমনেই একটি স্বপ্ন কল্পনা রচনা করে নিয়েছে। তাও আমি ভাবিনি। আজও ভাবিনে। তবে সেই বিশ্বাসেই যে আজ ছত্রিশ সাল থেকে তিপ্পান্ন সাল পর্যন্ত কাজ করছি তাও নয়। মনে মনে বিচার করে, এই কর্তব্য বলে করে যাচ্ছি। এই সতের বছর সেখানেই পড়ে আছি এই জন্যে।
কিন্তু সে থাক। যা বলছিলুম বলি।
মেজদি শেষকালে বলেছিলেন, বেশী মদ খেতে বারণ করেছিলেন। একবারে খাওয়া বন্ধ করতে বলেননি। বলেছিলেন, ওগুলো বেশী খাসনে ভাই। একেবারে না-খেতে বলব না। মাছের জল আর তোদের মদ। রায়বাহাদুর আমার শ্বশুর—তাঁর ঘরে সৌভাগ্যশিলা ছিল সন্ন্যাসীর দেওয়া, তার উপর যুগলবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষা নেবেন ঠিক করলেন। তা গুরু ছিলেন রামব্রহ্ম ন্যায়রত্ব। তিনি বললেন-তা হয় না। তবে ব্যবস্থা আমি করে দিচ্ছি। যিনি শ্যাম, তিনি শ্যামা। শক্তিমন্ত্রের যুগলে দীক্ষা দিলাম। তুমি বৈষ্ণববীজে জপ করো। আর পিতলের বাটীতে নারকেল জল ঢেলে তর্পণ করে তাই প্রসাদ নিয়ো। লোকে বলে, তাতেই নাকি রায়বাহাদুরের নেশা হত। তা অল্প করে খাস। আর বিয়ে করে ফেল। সেই সুলতাকেই না হয় বিয়ে কর। ধনেশ্বরেরা আপত্তি-টাপত্তি করবে। মামলা- মকদ্দমা করবে। তা তুই না হয় সেবাইতী ছেড়ে দিবি। দেবোত্তরে তো আছে ছাই। সম্পত্তি তো পত্তনী দিয়ে সব তোর হাতে। কলকাতায় গিয়ে থাকবি।
আমার মনে সুলতা ওই গোপাল সিং-এর বংশধর শিবু আর বীরেশ্বর রায়ের প্রপৌত্র শিবেশ্বর রায়ের ছেলে অতুলের কথা নতুন করে জেগে উঠল।
বললাম সে হবে ঠাকুমা। তুমি আগে খালাস হয়ে বেরিয়ে এস, তখন হবে।
তিনি বলেছিলেন—না রে, দেরী তুই করিসনে। আমি খালাস হয়ে এসে তোর বউয়ের কাছে উঠব, বুঝলি? ওরে বউ নইলে সংসার আলোনা হয়ে যায়। বউ চিনির মত মিষ্টি নয় রে, নুনের মত মিষ্টি। বিয়ে করলে বুঝবি—জীবনের অন্নের ওপর ব্যান্নন পড়ল। মানে-অভিমানে চাটনীর স্বাদ পাবি। ছেলে-মেয়ে হলে তার ওপর পায়েস মিষ্টি পড়ে ভোগ ষোল আনা হবে। নইলে তুই আবার যে কি করবি, তা ভগবানও বলতে পারবেন না।
হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে কিছু মনে করেই যেন সুরেশ্বর হেসে আপনমনে ঘাড় নাড়তে লাগল, যে ঢঙের হাসির মধ্যে অর্থ একটাই, সেটা হল- হায় হায় হায়! এ হায় হায় আপসোসেরও বটে, আবার তারিফেরও বটে। কোন মৃত প্রিয়জনের সুখস্মৃতি মনে হলে যেমন হাসি হাসে মানুষ।
সুলতা প্রশ্ন করলে কি?
—হাসছি কেন জিজ্ঞাসা করছ?
সুলতা বললে, শুধু তো হাসছ না, তার সঙ্গে আরও কিছু রয়েছে।
সুরেশ্বর বললে-ধরেছ ঠিক। ভাবছি টাকার দেনা যথাসর্বস্ব দিয়েও শোধ হয়। তাতে খালাস পেয়ে মানুষ খেটে-খুটে নতুন করে শুরু করতে পারে, যাতে আর পাওনাদারের দাবী চলে না। কিন্তু কাজের দেনা, কর্মফলের জের, ওর আর শেষ নাই। শেষ হয় না। এমন টাকার দেনায় মহাজন মাফ দেয়, না দিলে দেউলে হয়ে রেহাই মেলে, কিন্তু এতে মাফ নেই, আর দেউলে আইনের মত আইনও নেই!
সুলতা হেসে বললে—অর্থটা কি? রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায়ের বংশের ছেলে আর ঠাকুরদাস পালের বংশের মেয়ে ওই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একত্রিশ-বত্রিশ সালে প্রেম করেছিল, তারপর ছত্রিশ সালে সরে গিয়েছিল এবং আবার তিপ্পান্ন সালে সারারাত্রি জেগে বোঝাপড়া করছে?
—বলতে পার—
বাধা দিয়ে সুলতা বললে —সেজন্যে কিন্তু আমি আসিনি। আমি শুনতে এসেছিলাম, কীর্তিহাটের রায়বংশের ইতিহাস, দেখতে এসেছিলাম তোমার ছবি। কত উজ্জ্বল করে তুমি তাকে তুলে ধরে আর্কিওলজিক্যাল মনুমেন্ট তৈরী করছ। ফৈজী বলে এক নাচওয়ালীকে নবাব সিরাজুদ্দৌলা ঘরের ভেতর পুরে জানালা-দরজা গেঁথে মেরেছিল। বন্ধ ঘরটা আজ হয়তো খোলা। লোকে দেখে ঘরখানার গড়ন, নক্সা, বাহার আর তারিফ করে। দেখতে গেলে দরজায় টিকিট কিনতে হয়।
সুরেশ্বর বললে, না। ও-পথ ধরে আমার মন হাঁটেনি সুলতা। তুমি পলিটিক্যাল মানুষ, তুমি নিজে যখন ‘ইনকিলাব জিন্দাবাদ’ হাঁক, তখন ঠিক অর্থ ভাব-বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক। কিন্তু পথেঘাটে বা কোথাও ওই হাঁক শুনলে চমকে ওঠো, ভাবো—কম্যুনিস্টরা হাঁক দিচ্ছে। ওর আসল অর্থ, তারা ছাড়া বাকিরা সকলেই বিপ্লবের মধ্যে রক্তের স্রোতে ভেসে যাক।
সুলতার মুখ লাল হয়ে উঠল, সে কিছু বলতে যাচ্ছিল। সুরেশ্বর হাতজোড় করে বললে—মাফ চাচ্ছি। আমাকে ভুল বুঝো না সুলতা, আমি তোমাকে বাঁকা বড়শিতে বিধতে চাইনি। বিচারকের আসনে বসিয়েছি তোমাকে। তুমি বিচার করো। দেখ—স্যার গুরুদাস তখন উকীল হাইকোর্টে, এক জজ বলেছিলেন, হাফ এডুকেটেড বার। গুরুদাসবাবু পাদপূরণ করে বলেছিলেন, এ্যান্ড কোয়ার্টার এডুকেটেড বেঞ্চ। এটা অনেকটা তেমনি হয়ে গেছে। যে-হাসি দেখে তুমি তোমার আমার কথা তুললে, তা আমি ভাবছিলাম না। ভাবছিলাম, ওই গোপাল সিং-এর আর রায়বংশের বিবাদের কথা। সেটা অতুল আর মেজদির আর্মস অ্যাক্টের কেসে কনভিকশনেও শেষ হয়নি, তারপরও তার জের চলেছে। এই সেদিন পর্যন্ত। তারপর মেজদি বলেছিলেন, বিয়ের কথা। আমি মামলা করেছি, সে আমার উপর হামলা করেছে। তাতেও—
হাসলে সুরেশ্বর।
হেসে বললে—তাতেও ঠিক এই তত্ত্বটা সত্য হয়ে গেছে যে, কর্মফল না বল, ক্রিয়া- প্রতিক্রিয়ার জের মেটে না দুনিয়ায়। আরও মজার কথা শোন, সেইদিনই বিশ্রীভাবে ঠিক এমনি আর একটা মামলার নোটিশ জারী হয়েছিল। ঠিক এই কারণেই ওই হাসিটা আপনি এসেছে এবং আমি মনে মনে তারিফ করেছি কর্মফলের খেলার।
মেদিনীপুর থেকে বাড়ী এসে মুখ-হাত ধুয়ে গ্লাসে ব্র্যান্ডি ঢেলে জল মিশিয়ে খাচ্ছি, হাতে সিগারেট পুড়ছে। আর ভাবছি, যতদূর মনে পড়ছে এলোমেলো ভাবনা। গোপাল সিং, বীরেশ্বর রায়, রাম সিং, শিবেশ্বর রায়, হরি সিং, শিবু, অতুলেশ্বর, মেজদি; মনের মধ্যে ক্ষোভ ধোঁয়াচ্ছে। কখন যে অজ্ঞাতসারে রায়বংশের জমিদারত্ব বেরিয়ে এসে তাতে ফুঁ দিতে লেগেছে বুঝতে পারিনি। মনে সংকল্প করছি—আজও হরি সিংরা আমাদের প্রজা। আমলটা উনিশশো ছত্রিশ হোক, এখনও পারমানেন্ট সেটেলমেন্ট রাইট অনুযায়ী ওদের গাঁয়ের ঊর্ধ্ব-অধঃ হক হুকুকায় মালিক আমি। এদিকে সেটেলমেন্ট এসেছে। আমার জমিদারী স্বত্বের অধিকারে আমি হরি সিংয়ের সমস্ত রায়তীস্বত্বে লাখরাজ থাকলে, লাখরাজ স্বত্বে আমি আপত্তি দিতে পারি। এর আগে যদি আমার কর্মচারীরা তাতে সায়ও দিয়ে থাকে, তবে তাতে আমি গররাজী হয়ে আপত্তি জানাতে পারি যে, কর্মচারীর সঙ্গে যোগসাজস করে এ-সম্মতি দেওয়া হয়েছে, এটা আমি অস্বীকার করছি। সেটেলমেন্ট কোর্ট না মানে, আমি দেওয়ানীতে মামলা করতে পারি। মুন্সেফ কোর্ট, জজকোর্ট, হাইকোর্ট পর্যন্ত এ-মামলা চলতে পারে। অনেক কিছু চলতে পারে। এমন কি কীর্তিহাট স্কুলের ছেলেদের উত্তেজিত করে ওই শিবুর জীবন দুর্বহ করা যেতে পারে।
পায়ের শব্দ শুনে গ্লাসটা তাড়াতাড়ি শেষ করে নামিয়ে দিয়ে রঘুকে বললাম, নিয়ে যা এখান থেকে। লোকজন আসছে।
প্রথমেই এল অৰ্চনা। খবরটা প্রকাশ হতে বাকি ছিল না। খবর সবাই জেনেছিল। অৰ্চনাও জেনেছিল, সে এসে ঘরে ঢুকেই মুখে কাপড় চাপা দিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বললে-এ কি হল সুরোদা! ঠাকুমা—
বুঝলাম, মেজদির জেলটা তার জন্যে এই ভেবে মেয়েটা মনে মনে নিজেকে নিজে প্রহার করছে। আমি বললাম—মেজদি তোকে কাঁদতে বারণ করেছে অর্চি। তুই কাঁদিসনে। তিনিও বলেছেন, আমিও বলছি, তুই যা করেছিস, তা রায়বাড়ীর আর একটা ছেলে যদি করত—ধর আমি করতাম তবে রায়বংশের মুখ দ্বিগুণ উজ্জ্বল হত। তুই মেয়ে, কুমারী, তাই। মেজদি বললেন কি জানিস, তাঁকে স্বপ্নে মেজঠাকুরদা দেখা দিয়ে বলেছেন যে, তুই হলি এ-বাড়ীর সতী বউ ভবানী দেবী। কিন্তু এখন থেকে সাবধানে থাকিস ভাই। দেখ হিন্দুর ঘরে কন্যা হল লক্ষ্মী, তার মর্যাদাতে বংশের মর্যাদা।
অৰ্চনা হঠাৎ বললে—আমি যাচ্ছি সুরোদা। সব দলবেঁধে আসবার কথা। বড় জ্যেঠামশাই সন্ধ্যে করছেন, তাঁর হলেই সব আসবে। আমার বাবা আজ এসেছেন। তিনিও আসবেন। পালাই। ওর যাবার একটা পথ ও আবিষ্কার করেছিল। ওই কাঁসাইয়ের ঘাটের দরজা দিয়ে। যেতে গিয়ে অর্চনা ফিরে এল। এসে চাপাগলায় বললে, সুরোদা, নদীর ওপারে একটা লোক।
—লোক?
—হ্যাঁ, অদ্ভুত পোশাক। কোট-প্যান্ট বটে। কিন্তু কি রকম!
—তুই সদর দরজা দিয়েই যা না। অপরাধ তো করিসনি। খোঁজ নিতে এসেছিলি, তাতে হয়েছে কি? যা। রঘু বরং তোকে পৌঁছে দিয়ে আসুক।
তাই সে গেল। আমি দেখতে গেলাম লোকটা কে? গিয়ে দাঁড়ালাম ছত্রির গোল ঘরটার। সন্ধ্যে পার হয়ে গেছে, শীতকালের শেষ; মেজদিদের মামলা গড়িয়ে গড়িয়ে ছত্রিশ সাল পার করে সাঁইত্রিশ সালের মার্চের কাছে এসে পৌঁচেছে। বাংলা ফাল্গুন মাস, শুক্লপক্ষের গোড়ার দিক, জ্যোৎস্নায় দেখতে পেলাম, হ্যাঁ, দস্তুরমত একটা কোট-প্যান্ট-পরা লোক ওপারে জঙ্গলের ধারে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে।
আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কে ওখানে? ওখানে দাঁড়িয়ে কে?
বেশ মোটা গলায় উত্তর এল-From that Goan Para.
—গোয়ানপাড়া? কে তুমি? গোয়ানদের কে?
—Oh—I am none of them.—তারপর ফিরিঙ্গীসুলভ ভাষায় বললে-উ লোকের—হিলডার—মেহমান আছি। Come from Calcutta.
—কি করছ ওখানে? এমন করে দাঁড়িয়ে?
—Who you please? হামি রয়বাবুকে সাথ মুল্কাত মাতা হ্যায়। Are you Roy Babu-Mr. Sureswar Roy?
বললাম—Yes that’s my name.
—Thank God—May I see you sir?
রঘু এসে বললে—ও বাড়ীর সব আসিয়েসেন।
—ও! চল। বলে ওকে বললাম- Come tomorrow sometime.
—Why not today?
—No. I am very tired today. Come tomorrow. Come with Roser or Gomesh. They belong to Goanpara,
বলে আমি চলে এলাম।
নীচে তখন ধনেশ্বর কাকা, জগদীশ্বর কাকা, বিমলেশ্বর কাকা, এমন কি গাঁজাখোর ঘোরতর বাউণ্ডুলে কমলেশ্বর সেও এসেছে। সুখেশ্বর কাকার দুই ছেলে, কল্যাণেশ্বর, ধনেশ্বর কাকার মেজছেলে রাজেশ্বর, ছোট-বড় সকলেই এসেছে। এবং সেদিন একটা নতুন চেহারা দেখলাম রায়বংশের সবারই মধ্যে। আগুনে ক্রমশ ছাই পড়ে, পড়তে পড়তে এমন হয় যে, উপরে শুধু ছাই আর নীচে কাঠকয়লা কি পোড়া কয়লা ছাড়া কিছু থাকে না। কিন্তু সেদিন দেখলাম এই মামলাটার ঝড়ো হাওয়ার ছাই উড়ে গেছে, নিঃশেষ হয়ে এবং কাঠকয়লাগুলো দামী কাঠের কয়লা বলে গভীর নীচে যে এক টুকরো আঙরায় আগুন ছিল, তার আগুন কাঠকয়লাগুলোতেও হাওয়ার জোরে কোণে কোণে ধরে উঠে ঝিকমিক করছে। অতুলের আগুনের ছোঁয়াচে ওরাও যেন ধরে উঠেছে।
ধনেশ্বর কাকা আজ আর আক্ষেপ করলেন না। রায়বাহাদুরের বংশধর জেল খাটছে, তাতে তিনি ক্ষুব্ধ হন নি।
সকলেই দুঃখ পেয়েছেন। চোখে-মুখে তারই ছাপ ছিল। টুকরো-টুকরো ছাড়া ছাড়া কথা হল।
—আপীল?
আমি বললাম—আপীল করব বইকি।
—আপীল মিথ্যে! এত বড় সাদা শয়তানের জাত, এ তো হয় না!
জগদীশ কাকার কথা তোমাকে বলেছি। গাঁজা, মদ দুই তিনি খেতেন। ক্রোধ তাঁর প্রচণ্ড। প্রথম যৌবনে অহরহ বন্দুক ঘাড়ে করে বেড়াতেন। পথে কোন লোকের, বিশেষ শুদ্র প্রজাদের, প্রণাম করতে আধ মিনিট দেরী হলে মাথার চুলের মুঠো ধরে মাটিতে ঠেকিয়ে দিয়ে বলতেন—প্রণাম করতে হয়। বুঝেছিস? হ্যাঁ!
তীর্থ থেকে সেই দিনই ফিরেছেন; শালা রেলের চাকরি করে, ছোট চাকরে নয়, তার কাছ থেকে সেকেন্ড ক্লাসের পাস নিয়ে ভারত ভ্রমণ করে ফিরেছেন। বিদেশের হাওয়ায় তাঁর চেহারা উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। তিনি এখন অনেকটা সুস্থ। হয়তো তীর্থের প্রভাব ছিল। তিনি বললেন—অন্তত মাকে দণ্ডটা বিনা দোষে দিয়েছে। ওরা যাবে। যেতে হবে। এ আমি বুঝে নিয়েছি। দেখে তো এলাম, গোটা ভারতবর্ষ! আপীল তুমি কর বাবা সুরেশ্বর। করলে হয়তো অন্য রকম দাঁড়াবে। শুধু মায়ের জন্যে। ওই। উনি সন্তানের মত মানুষ করেছেন অতুলকে; বলতে গেলে ওঁরই ছেলে। সে রাখতে দিয়েছে, সরল বিশ্বাসে রেখেছেন।
কল্যাণেশ্বর বললে—এটা মেজকা ভাল বলেছেন। অতুলকার জেলেই বরং থাকা ভাল। বেরিয়ে এসে ও তো চুপচাপ থাকবে না! হয়তো জেল থেকে বেরিয়ে এমন কিছু করবে যে, ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে দেবে।
ধনেশ্বর কাকা বলেছিলেন—কল্যাণ এটা ভাল কথা বলেছে। এতক্ষণে হঠাৎ তাঁর কথায় অ্যাক্টিংয়ের সুর লেগেছিল, খুব ভাল কথা। দু-রদৃষ্টির কথা! আর আজকের কালে রাজদ্রোহিতার জন্য জেল সে তো সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরবের কথা! মানুষে ধন্য ধন্য করবে, পরলোকে পিতৃপিতামহের মুখ উজ্জ্বল হবে। ওঃ! কে জান ও, ওই শৈশবে মাতৃহীন ছেলে, মাতৃস্তন্যের জন্য কাঁদত, ছোটমা বুকে তুলে নিয়েও ওটা দিতে পারেন নি। তিনিও কাঁদতেন তার সঙ্গে। সেই শিশু। ওঃ! রায়বংশ জমিদার বংশ। সাহেব কুলের অনুগৃহীত বশম্বদ, I remain your most obedient servant, এটা A B C শিখবার আগেই মুখস্থ হত আমাদের। সাহেবরা এসে এই বিবিমহলে থাকত, খানা খেত, আমরা দেখেছি, কর্তারা তটস্থ। সেই বংশের ছেলে। উড়ায়েছে বিদ্রোহের ধ্বজা। স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়!
সুলতা, তোমাকে শপথ করে বলতে পারি, আমার মনে রয়েছে স্পষ্ট, এই ধরনের থিয়েটারী ঢঙে ধনেশ্বর কাকার কথাগুলো সেদিন এতটুকু অশোভন বেমানান মনে হয় নি। বরং মনের মধ্যে প্রতিধ্বনি তুলেছিল। তাতে আন্তরিকতার ঝঙ্কার ছিল।
হঠাৎ কমলেশ্বর একটু বেসুরো বলেছিল, ক্রুদ্ধ হয়ে বলে উঠেছিল—ওই হরি সিংকে আমি দেখব। এর শোধ নেব!
ধনেশ্বর কাকা ধমক দিয়ে বলেছিলেন—দেখ, নেশা রায়বংশে প্রায় সবাই করেছে। কিন্তু তোর মতো মাথা খারাপ কারুর হয় নি। ওই নিয়ে আস্ফালন করে বেড়াস নে। তাছাড়া সেটা তো কীট রে! কুক্কুর! মাসিক সাত টাকায় তার খোরাক পোশাক!
কমলেশ্বর প্রতিবাদ করে বলে উঠেছিল—আমি আজ তিন দিন প্রতিজ্ঞা করে নেশা পরিত্যাগ করেছি।
জগদীশ কাকা বলেছিলেন, মঙ্গল হবে তোর। কিন্তু যা বললি তাতে মঙ্গল হবে না। বুঝতে চেষ্টা করিস, অতুল কি করেছে। আমাদের পূর্বপুরুষ ইংরেজের দাসত্ব স্বীকার করেছিলেন। অতুল সেটা ছিঁড়ছে। সে ছিঁড়ছে, শেয়াল কুকুর মেরে নয়। সিংহ, বৃটিশ সিংহের সঙ্গে তার যুদ্ধ!
সেই দিন সুলতা, সেই মুহূর্তে নতুন করে সেই একখানি ছবি আঁকবার কথা মনে হয়েছিল। সেই একদিকে বীরেশ্বর রায়, রত্নেশ্বর রায় ইউনিয়ন জ্যাক ধরে দাঁড়িয়ে আছেন, অন্য দিকে অতুল তেরঙ্গা ঝাণ্ডা ধরে দাঁড়িয়েছে।
সেই আমার ছবি এঁকে এই জবানবন্দী রচনার শুরু।
ওঁরা চলে গেলে, আমি ওই ছবির কথাই ভাবছিলাম। শরীর ক্লান্ত, তবু মন ক্লান্ত হয় নি। আবার খানিকটা ব্র্যান্ডি খেয়ে জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়িয়ে মনে মনে ছবির খসড়াই করছিলাম। হঠাৎ ডাক শুনলাম—
—সাব। রয় সাব! বাবু সাব!
সেই কণ্ঠস্বর। মোটা কর্কশ। খানিকটা উদ্ধত!
—মিস্টার রয় সাব!
সদর দরজায় ডাকছে এবার। বিরক্ত হয়ে রঘুকে বললাম-ডাক তো লোকটাকে!
ভাবছিলাম ওকে কঠিন তিরস্কার করব!
কিছুক্ষণ পর ভারী জুতোর শব্দ তুলে এসে দাঁড়াল একটি মূর্তি। হ্যাঁ, লোক বললে ঠিক বলা হয় না। হিন্দীতে বলে, ‘এক মূরত’। এও তাই। বিচিত্র বিস্ময়কর। যত বিরক্তি হয় দেখে, তত কৌতূহল আকর্ষণের একটা শক্তি আছে লোকটির মধ্যে।
সে মানুষটা যেন মানুষ নয়, বিচিত্র গড়নে গড়া মানুষের একটা নিদর্শন। মডার্ন স্কাল্পচারে যে সব মূর্তি গড়ার রেওয়াজ উঠেছে এ যেন তাই। বিধাতার শিল্পশালায় নানা ছাঁচ আছে। অষ্টাবক্র মুনির কথা শোনা যায়, তাও দু’চারটে দেখা যায়। কিন্তু এ ছাঁচও কি বিধাতার শিল্পে আছে? অত্যন্ত ভারী গড়ন, লম্বাও কম নয়, কিন্তু তবু কেন যেন অস্বাভাবিক অসদাচার, চোখ দুটো উগ্র এবং গোল নাকটা স্কুল; ঠোঁট পুরু। উজ্জ্বল হেজাক লণ্ঠনের আলো তার মুখে পরিপূর্ণভাবে পড়েছিল, রঙটা দেখলাম লালচে কিন্তু রোদে পুড়ে তামাটে হয়ে গেছে! একজোড়া বেশ পাকানো গোঁফ লোকটাকে আরও উদ্ধত চেহারা দিয়েছে। পোশাকটা পুরনো, এবং দেখেই, বোঝা যায় পোশাক ওর মাপে তৈরী পোশাক নয়, কলকাতার চোরাবাজার যাকে বলে, সেখানে যে সব পুরনো পোশাক ফুটপাথে গাদা ক’রে বিক্রী করে, তা থেকে কেনা। অথবা অনেকদিনের পুরনো। কারণ সবই খাটো হয়ে গেছে। অথচ লোকটা খুব হৃষ্টপুষ্ট নয়, খাদ্যাভাব আছে এটা খুব স্পষ্ট। বয়স বেশী নয়—বড়জোর চল্লিশ হবে।
লোকটা এসেই অভিবাদন করলে গুড ইভনিং স্যা—
বললাম—গুড ইভনিং! কিন্তু তোমাকে তো আমি বললাম —কাল আসবার জন্যে। কিন্তু তুমি তবু এ সময়ে কেন এলে?
লোকটি বললে—I am sorry sir-believe me—I am so sorry for this.
লোকটার কথার উচ্চারণও ওর চেহারার মত ভারী। জিভটা মোটা, সরি ‘অড়ি’ গোছের উচ্চারণ করে ফরকে শুধু ফ বলে শেষ করে। খুব বিনয় করে বললে কিন্তু তা আমাকে খুব খুশী করতে পারেনি সেদিন সেই মুহূর্তে। আমার মাথায় তখন মদের প্রভাবে মস্তিষ্কের স্নায়ু-শিরা উত্তেজিত হয়ে উঠেছে এবং অন্যমুখী হয়েছিল। যে কল্পনাটা মাথায় কিছুক্ষণ আগে এসেছিল সেটা তখন বাইরের এই ব্যাঘাত সত্ত্বেও যাদুকরের বীজ থেকে অঙ্কুর, অঙ্কুর থেকে পাতা, তা থেকে গাছ হয়ে বেড়ে উঠছে, আবার মিলিয়ে যাচ্ছে, আবার গজিয়ে আর একটা চেহারা নিচ্ছে, এমনি অবস্থা। বীরেশ্বর রায় রত্নেশ্বর রায় আর দেবেশ্বর রায় ইউনিয়ন জ্যাক ইংরিজী ভাষা, ইংরিজী পোশাক আর এদিকে তেরঙ্গা ঝাণ্ডা, খদ্দরের কাপড় ধরে দাঁড়িয়ে আছে অতুল তার পিছনে মেজদি, হাতে গীতা, পরনে থান কাপড়—তার পাশে অর্চনা লালপেড়ে শাড়ী পরনে, তার হাতে আনন্দমঠ আর শাঁখ। আবার পরক্ষণেই ভাবছি—না দুটো স্বতন্ত্ৰ ছবি—শতবর্ষ আগে, শতবর্ষ পরে।
পরক্ষণেই মনে হল না! আরও একখানা ছবি। মিউটিনির কলকাতার ছবি না থাকলে এটা সম্পূর্ণ হয় না। কলকাতার মিউটিনির ছবি মনে ভেসে উঠল একখানা চিঠির বর্ণনা থেকে। নবাব ওয়াজিদ আলি শাকে যেদিন মেটেবুরুজ থেকে বন্দী করে ফোর্ট উইলিয়মে আটক করে ইংরেজরা, সেদিন ময়দানে বেরিয়েছিলেন বীরেশ্বর রায়। দৃশ্যটা তিনি দেখেছিলেন। তারপরই চলে আসেন কীর্তিহাটে।
ওইসব ফাইলের মধ্যে খানকয়েক চিঠি পেয়েছিলাম। একখানা কালীপ্রসন্ন সিংহ মশায়ের। একখানা বীরেশ্বর রায়ের মামাতোভায়ের।
১৮৫৭ সালের ১৩ই-১৪ই জুন কলকাতায় সে এক বিভীষিকার রাজত্ব। সিপাহীরা ব্যারাকপুর-বহরমপুরে বিদ্রোহী হয়েছে, কলকাতায় আসছে ভেবে লর্ড ক্যানিংয়ের বাড়ীর সামনে ইংরেজ ফিরিঙ্গী ক্রীশ্চানদের ভিড় জমেছিল। গঙ্গার বুকে জাহাজ সাজানো ছিল। সিপাহীরা এলে তারা জাহাজে গিয়ে উঠবে। বাঙালী হিন্দু মুসলমানের উপর বিশ্বাস তো বিশ্বাস এতটুকু আস্থা ছিল না। তাদের উপর আক্রোশে তারা ফেটে পড়তে চাচ্ছিল। বীরেশ্বর রায় তাই দেখেই কলকাতা ছেড়ে এসেছিলেন কীর্তিহাট। সাহসী বাঘ শিকারী প্রজাশাসক বীরেশ্বর রায় আমার পূর্বপুরুষ, তিনি ভীত হয়েছিলেন নাই বললাম-শঙ্কিত হয়েছিলেন এই কথাটার উল্লেখ রয়েছে কালীপ্রসন্ন সিংহের চিঠিতে। বীরেশ্বর রায় জানিয়েছিলেন তাঁকে তাঁর সংকল্পের কথা। উত্তরে সিংহ লিখেছিলেন,
“ডিয়ার বেরাদর, বেরাদরই লিখছি আপনাকে। বেরাদারি সহজ নয়, বেরাদারিতে একসঙ্গে শুধু আহার বিহার নয় পরস্পরের বিপদে আপদে বুক দিতে হয়। মরলে কাঁধ দিতে হয়। সুখের ভাগ দিতে হয় দুঃখের ভাগ নিতে হয়। আপনি এ দুর্যোগে, এ দুর্যোগ আমাদের আশ্বিনে ঝড়ের মত (সাহেব বাহাদুরেরা যাকে সাইক্লোন বলে), এই সিপাহী মিউটিনির সাইক্লোনে কীর্তিহাটের ছাতার মধ্যে মাথা গুঁজবার ভাগ দিতে চেয়েছেন, এরপর বেরাদার না বলে উপায় কি!
আপনি এই ডামাডোলের বাজারে দেশে যাবার মতলব করেছেন—উত্তম করেছেন। তবে শুনেছি মেদিনীপুরে গোলমাল তাল আকারে না হলেও পাতিলেবু আন্দাজের আছে। তা সহ্য হবে। খবর পেয়েছি মেদিনীপুরের হেডমাস্টার রাজনারায়ণ বসু কাপড় চাদর ভিতরে পরে তার উপরে কোট পেন্টালুন চড়ান। সিপাইরা এলেই পেন্টালুন কোট খুলে ফেলে দেশী চেহারায় সেপাইদের জয় হাঁকবেন। আপনার বাড়ী অনেক ভিতর অঞ্চলে। আপনি অনেক সময় পাবেন। হয় মুসলমানী আমীর সেজে বসবেন নয় আপনার ঠাকুরদাদার কালীমার সামনে পৈতে বের করে মা কালী মা কালী বলে স্তব করবেন। বেরাদারের উপদেশ মনে রাখবেন। আমার বা আমাদের কলকেতার বাবুদের যাবার উপায় কি? এইখানেই যে আমাদের সব! মাগ ছেলে, ভিটে মাটি, টাকা পয়সা গিনি, দু’চারখানা হীরে মুক্তোভরা ভারী ভারী সিন্দুক, ঘরসংসার মায় গড়গড়া, রূপোবাঁধা হুঁকো পর্যন্ত। কলকাতায় জানবাজারে আপনার বাড়ীতে ইট কাঠ আছে, কীর্তিহাটে তার থেকে বড় বাড়ী। টাকা পয়সা কোম্পানীর কাগজ হীরে জহরত পুঁটলি বেঁধে নিয়ে কালী কালী বলে চলে যান সেখানে।
বাঙালী বিদ্রোহ কালে ভেতো বাঙালীর ইংরেজ এবং ফিরিঙ্গীদের বিরুদ্ধে তীব্র শ্লেষ এবং ব্যঙ্গ বড় হয়ে উঠছে। ওদিকে চুনোগলি কসাইটোলার মেটে ইদরিস, পিরূস, গমিস, ফিরিঙ্গীরা ডিস্ খাবার লোভে ভলেনটিয়ার হয়েছে। সাহেবেরা শক্ত জায়গায় কিল মারতে ভয় খেয়ে নরম জায়গায় আঁচড়াচ্ছে। সেপাইদের উপর রাগ বাঙালীর উপর ঝাড়বার তালে আছে। লর্ড ক্যানিংকে বাঙালীর অস্ত্রশস্ত্র বঁটি কাটারি পর্যন্ত কেড়ে নিতে ওসকাচ্ছে। শুনেছেন বোধহয় গোপাল মল্লিকের বাড়ী সভা ডেকে বাঙালীরা বুঝিয়েছে যে, যদিও একশো বছর হয়ে গেল তবু তাঁরা সেই মেড়া বাঙালীই আছেন। ওদিকে ইংরেজরা মাগছেলে ও স্বজাতির শোকে মরিয়া।”* মরীয়া তেরিয়া হয়! সুতরাং কলকাতায় থেকে কি করবেন? বাঈজীর গান জমবে না। চোখে ব্র্যান্ডি হুইস্কির নেশা লালচে আভা ফোটাবে না। সুতরাং চলে যান—চলে যান।
[* কালীপ্রসন্ন সিংহের সিপাহী বিদ্রোহ সম্পর্কিত রচনার অংশবিশেষ।]
হ্যাঁ, শুনলাম, কাপ্তেন সুরো মল্লিক বললে—সোফি বাঈজী নাকি আপনাকে ছেড়ে একটা পাগলা সাধুকে ভজেছে? আপনি তাকে নাকি গলা টিপে ধরে প্রায় বোবা ক’রে দিয়েছেন। সে নাকি এখন খোনা সুরে আঁ-আঁ ক’রে কি বলে কেউ বুঝতে পারে না। সুরো মল্লিক বললে-এবার বাওয়া বীরেশ্বর রায় ফীরেশ্বর হয়ে যাবে। বলে, বাওয়া সাধু নাকি বেহ্মদত্যি নামায়। কাজটা মন্দ করেন নাই। আমার মতে তো সাতশো সাবাস আপনার পাওনা! সেদিন একটা ন্যাংটা নাগা এসেছিল ভিক্ষে চাইতে। একমুঠো চাল সে নেবে না। দুটো চাল হাতে নিয়ে দুই আঙুলে টিপে ঝরঝর করে জল বের করলে, চাকর বেটারা তাকে শিব সাক্ষাৎ ভেবে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ হল। আপনি যেমন পাগলটাকে উত্তমমধ্যম দিয়েছেন তেমনি দিতে পারলে আমি খুশী হতেম। তবে তাকে দুটোর বেশী পয়সা আমি দিই নি। হিসেব করে দেখলে দু পয়সার ম্যাজিক সে দেখিয়েছে তা মানতে হবে। শেষ হল কি জানেন, কোথা থেকে ঘোড়ায় চেপে সাহেব পুলিশ এসে তাকে ধরলে। তার কাছ থেকে বের করলে রুটি। এ রুটি নাকি সেপাইদের নিশানা! কি সব্বনাশ মশাই! আপনি চলে যান! গাঁয়ে দেশে ঘরবাড়ী থাকলে আমিও পালাতাম।
ইতি
ভবদীয় বেরাদার
কালীপ্রসন্ন সিংহ
সেদিন রাত্রে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে পত্রখানাকে স্মরণ হয়েছিল। তার মধ্যে নতুন করে অঙ্কুর মেলে ছবির আইডিয়া আর একরকম চেহারা নিচ্ছিল।
আমি ছবি আঁকি। আমি সেকালের ছবির কথা ভাবছিলাম। বাংলাদেশের পটের মাকালী, রাধাকৃষ্ণ, নরকের ছবি বাতিল হয়ে তখন ইংরেজী ছবির ঢঙ এসেছে। কলকেতার এবং বড় বড় রাজরাজড়ার বাড়িতে কুইনের অয়েল পেন্টিংয়ের আমল। আমি ঢঙের কথা ভাবছিলাম। মনে পড়ছিল দিল্লীর দরবার।
সাহিত্যে তখন বিদ্যাসাগর মশায়ের কাল চলছে। বঙ্কিমের আনন্দমঠ আসতে তখনও অনেক দেরী। অবনীন্দ্রনাথ নন্দবাবু যামিনী রায় অনেক পরে। আমি ভাবছিলাম দিল্লীর দরবারের ঢঙে আঁকলে কি হয়? হঠাৎ আমার চিন্তায় ব্যাঘাত দিয়ে লোকটা জোরে বারকয়েক কাশলে গলা ঝাড়া দিলে। আমি ফিরে তাকালাম। দেখলাম সে আমার দিকেই তাকিয়ে আছে। এবার মনে পড়ল ও কয়েকটা কথা বলতে চায়। জানালা থেকে সরে এসে আবার চেয়ারে বসে বললাম—বল তোমার কি বলবার আছে।
সে বললে—you see Roy Babu I am a poor man, very poor.
—হ্যাঁ সেটা দেখছি। কিন্তু কি চাও তুমি? সাহায্য? ওরে রঘু, একে দুটো টাকা দে তো!
লোকটা বললে—Oh God —আপনে হামাকে বেগার ভাবছে রায়বাবু। সো হামি নেই। বহুত দো রুপেয়া two rupees—আমি বকশিশ দিয়েছি খুঁজি লোককে!
—খুঁজি? বিস্ময়ের সঙ্গে আমি প্রশ্ন করেছিলাম—
—ও স্যার, I was a professional Shikari—pig বাবুর্চি জমিন্দার ব্যারিস্টার রইস আদমী—some times European sahibs were my clients. উলোককে শিকার মিলায় দিতম! মাচান কে পর উ লোকের Side এ থাকতম। Sometimes Roy Babu—I killed tiger for them, they used to pay me handsomely and carried the trophy as their own. তো ট্রাইব্যাল People বুনো আদমী যো লোক টাইগার ভাল্লু বাইসনকে খবর লিয়ে আসে খোঁজ দেয়—উ লোক—we call them—“খুঁজি”। Informer. I earned a lot and spent everything, sometimes I paid ten rupees to them. Two rupees নিয়ে কি হোবে আমার। No, I dont want money from you. I have not come to you fo’ that (নো-আই দোস্ত ওয়ান্ত মনি ফ্রম য়ু। আই হ্যাভ নত কম তু য়ু ফ দ্যাত।)
–Then (দেন)? একটু তিক্ত বিস্ময়ের সঙ্গেই প্রশ্ন করলাম আমি।
সুলতা বাধা দিয়ে বললে—এসব কথায় তোমার জবানবন্দি বড় বেশী জটিল ক’রে তুলছ সুরেশ্বর। রাত্রি শেষ হয়েছে। ভোর হয়েছে, পাখী ডাকছে। আমার তো যাবার সময় হয়ে গেল। সে হাসলে একটু।
সুরেশ্বর বললে—শিবের মাথায় জটা আছে সুলতা, গঙ্গার ধারা যে গঙ্গার ধারা তাও হারিয়ে গিয়েছিল, সেই জটার মধ্যে। জটা বাদ দিয়ে শিব অথবা গঙ্গা কারুর কথাই বলা যায় না। যা বলছি তা ওই সেকালের একশো জটার একটা জটা, যার মধ্যে দিয়ে রায়বংশের কাহিনীর স্রোত চলে এসেছে। এবং তোমার বংশের স্রোতেরও তার সঙ্গে সংস্পর্শ আছে। সেদিন রায়বংশের শরিকদের সঙ্গে যে সব কথা হয়েছিল তা শুধু উল্লেখ করেই ছেড়েছি, বলেছি সেই কথাগুলো যা আমার ছবি আঁকার কল্পনাকে নতুন ক’রে জাগিয়ে তুলেছিল। এর কথা না বললেই নয়। শোন—যতটা সকাল হতে হতে শোনা যায় তাই শুনে যাও। বাকীটা না হয় বাকীই থাকবে।
সুলতা হেসে বললে—বল!
সুরেশ্বর বললে—লোকটি বললে—রায়বাবু, আপনে হিলডা পিজ গোয়ান বুড়ীকে জানেন! দ্যাট ওল্ড ওম্যান হামার নিস, সিস্টারস ডটারকে নিয়ে আসছে কলকাতাসে! হা-নেম ইজ কুইনি মুকুরজী! এ বিউটিফুল নাইস গাল। (Her name is Quinee Mookherjee-a beautiful nice girl.)
—হ্যাঁ আমি তাকে দেখেছি।
—ইজ সী নত এ বিউতিফুল নাইস গাল—( Is she not a beautiful nice girl)?
—হ্যাঁ। কিন্তু হিলডা বলছিল—সে তার আত্মীয়। বাপ মা মরার পর সে তাকে এখানে এনেছে!
—ইয়েস রয়বাবু, থ্যাঙ্ক হা ফ দ্যাত। দেয়া ওয়াজ নান তু লুক আফতা হা এ্যাত দ্যাত তাইম। আই ওয়াজ দেন ইন জেল—Yes Roy Babu. I thank her for that. There was none to look after her at that time-I was then in jail—
—জেল? সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলাম আমি।
—ইয়েস ইন জেল। আই ওয়াজ কনভিকটেড তু জেল ফ সেভেন ইয়ারস ফ কজিং দি দেথ অব এ ভীল গুন্দা—বাই স্ট্রাইকিং হিম উইথ দি বাহ্ অব মাই গান। হি এ্যাতড্ মি ফাস্ত। (Yes, in jail. I was convicted to jail for seven years for causing the death of a Bhil goonda by striking him with the butt of my gun. He attacked me first.)
বিবরণটা সে বলে গেল।
সি-পির জঙ্গলে তখন একরকম তার বাস ছিল। বিচিত্র জীবন। ষোল-সতের বছর বয়স থেকেই তার শিকারে নেশা। বারো বছর বয়সে কলকাতায় এক ইয়োরোপীয়ান টেনিস ক্লাবে ম্যানেজারের অ্যাসিস্ট্যান্ট হয়ে ঢুকেছিল। বল কুড়িয়ে কাজ শুরু, কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যেই তার পনের-ষোল বয়সে সে সব শিখেছিল। লনের কাজ থেকে টেনিস খেলা পর্যন্ত। লেখাপড়া সে করেনি—ভাল লাগত না। এই সময় উড়িষ্যার এক করদ রাজ্যের রাজা এসেছিলেন কলকাতা, টেনিস কোচ, গ্রাউন্ড সুপারভাইজার প্রভৃতির সন্ধানে-তাঁর রাজধানীতে টেনিস খেলার ব্যবস্থা করবেন; প্রথম শ্রেণীর ব্যবস্থা। রাজা তাকেও পছন্দ করেছিলেন। সেও গিয়েছিল কোচ এবং সুপারভাইজারের সঙ্গে। সেখানে গিয়ে টেনিস থেকে সে গিয়ে পড়েছিল মহারাজার শিকারের ব্যবস্থার মধ্যে। এটা তারও ভাল লেগেছিল বেশী। রাজা ছিলেন পাকা শিকারী। রাজা তার উপর ছিলেন সদয়। ছেলেমানুষ বলেও বটে এবং তার উৎসাহ ও আনুগত্যের জন্যও বটে। তিনি টেনিসের চেয়ে তাঁর প্রিয়তর ব্যসন—শিকারের বিভাগে তাকে নিয়েছিলেন। সেও সেখানে তার কাজ দেখিয়েছিল। বন্দুক সাফ করা থেকে বন্দুক চেনা বন্দুক চালানো সবেই সে পাকা হয়ে শেষে পাকা শিকারী হয়ে উঠেছিল। রাজা হঠাৎ মারা গেলেন—প্রিন্স শিশু, পাঁচ বছরের। সুতরাং শিকার পার্টিতে ছাঁটাই হল। বন্দুক তাকে উঠল। ওর চাকরি গেল। চাকরি গেল কিন্তু শিকারের নেশা গেল না। সে নিজেই ব্যবসা খুললে। প্রফেশনাল শিকারী হল সে।
সুরেশ্বর বললে-তার কথাগুলো মনে পড়ছে সুলতা। সে বলেছিল—এ নেশা মদের নেশার চেয়েও নাকি তীব্র। এমন কি।
একটু বিনীত হেসে বলেছিল—If you allow me to say—তাহলে নারীর নেশার চেয়েও তীব্র। Stronger than woman hunting.
আমি হেসে বলেছিলাম—প্রথমটা জানি। দ্বিতীয়টা জানি না। কিন্তু থাক না ওসব কথা। যা ঘটেছিল তাই বল না।
সুলতা লক্ষ্য করলে সুরেশ্বর যেন হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে গেছে। সে তাকাচ্ছে তার ছবিগুলোর দিকে।
সময় চলে যাচ্ছি। ভোর হয়ে এসেছে। সুলতা শুনতে পাচ্ছে রাস্তার জল দেওয়ার শব্দ উঠছে। পাখি ডাকছে। কাক ডাকছে। শালিক পাখীদের কলকল শব্দে ডাক উঠছে। চড়ুইগুলো কিকিচ্ করছে। ক’টা চড়ুই ঘরটার মধ্যেই উড়ে বেড়াচ্ছে। এরা যে ঘরের কোন ফাঁক দিয়ে ঢুকে ঘরের মধ্যে বাসা বাঁধে কেউ বলতে পারে না।
সুলতা ডাকলে-সুরেশ্বর!
সুরেশ্বর তার দিকে তাকিয়ে বললে—ওই কথাটা ব’লে সেদিন আমি চমকে উঠেছিলাম সুলতা। রায়বংশের ইতিহাস মনে পড়েছিল। এ নাকি প্রকৃতির অভিশাপ! যাক। আমার সে চমক লোকটির চোখে পড়েনি। সে বলে যাচ্ছিল। প্রফেশনাল শিকারী হয়ে উড়িষ্যা এবং সি-পির বর্ডারের জঙ্গলে একটা জংলীদের গ্রাম থেকে কিছু দূরে একটা কাঠের বাংলো তৈরী করে সে শুরু করেছিল তার বিজনেস।
হ্যাঁ, বিজনেসই বটে। সে শিকারের সিজনের শুরুতেই কলকাতায় বড় বড় জমিদার ব্যারিস্টারদের কাছে যেত এবং বলত তার সঙ্গে গেলে শিকার গ্যারান্টিড। শিকার সে করিয়ে দেবেই!
—My arrangements were very good, Roy Babu and were liked by all big roycee people. Tigers, bears-leopards-they got. They also got girls—there. Anglo- Indian girls. I took them from Calcutta—for this purpose. They were sports. And-they had good time there. Forest was beautiful and full of thrill. Also they could earn a lot from these big people. They were my friends also.
আমি বলেছিলাম—ও কথা আবার আনছ কেন? যা বলবার তোমার তাই বল।
সে বলেছিল—
I don’t want to hide any thing from you sir, this is the reason why I am telling you everything. I was a dare-devil at that time. My mother did not like me. I did not care for her. She lived in Calcutta-in a house on the Eliot Road. The house belonged to her first husband-father of my elder sister. She was then in a convent. She loved me. I also loved her. This Quinee is her daughter Roybabu.
লোকটি কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ বিষণ্ণ হয়ে গিয়েছিল। আমার আগ্রহ খুব ছিল না তার কথা শুনবার জন্যে। তবু এই বিষণ্ণতার মধ্যে তাকে কোন প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হয় নি। স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম লোকটির কিছু মনে পড়ে গেছে।
তাই বটে—সে কয়েক মুহূর্ত পরেই বললে—কুইনি ছেলেবেলা থেকেই খুব শান্ত। আমি তাকে প্রথম যখন দেখি সে তখন বছরখানেকের বাচ্চা। ভারী সুন্দর শান্ত বেবী। একটু shy, একটি রঙীন কাঠবেড়ালী ছিল আমার। সর্বদা পকেটে থাকত। সেইটেকে দিয়ে ওর সঙ্গে আলাপ করেছিলাম। আমার মা হাঁ-হাঁ করে উঠেছিল। কামড়ে দেবে আঁচড়ে দেবে। আমি কাঠবেড়ালীটির মুখে আমার কড়ে আঙুল পুরে দেখিয়ে দিয়েছিলাম-সেটা কামড়ায় না। নিজের খোলা হাতের উপর চাপিয়ে দেখিয়েছিলাম, একটি নখের আঁচড় দেয় না। তাতেও মা থামে না।
My mother never liked me you see. I also did not like her. Whenever we met-we quarrelled. But my sister-oh she was an angel.
ওই কারণেই আমি আরও ঘর ছেড়েছিলাম। বাড়ীখানা তো আমার বাবার ছিল না, ছিল মানির বাবার। মানির বাবা ওই বাড়ী আর টাকা রেখে গিয়েছিল, সেই টাকায় ছেলেবয়সে মানি Convent-এ পড়ত। আর আমি ঘর ছেড়ে বনে বনে ঘুরতাম। To be frank—Mr. Roy—এটা আমার প্রকৃতিও বটে। আমার বাবার প্রকৃতি এমনি ছিল। মানি—
আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম-মানি? তোমার বোনের নাম নাকি? মানি?
—Yes Roy Babu, in not an English word it is a Bengali word- meaning-Jem-diamond. Mani’s father-so far I have heard-he had some Bengali connection. My mother though an Anglo Indian could speak Bengali like in as Bengalee.
—জান মানির যখন বিয়ে হল সে বিয়ে করেছিল একজন বেঙ্গলী ক্রীশ্চানকে—মিঃ মুকুজীকে—তখন মা আমাকে জানায় নি। জানিয়েছিল আমাকে মানি। আমি আসতে পারি নি। আসি নি। পরে এসে আলাপ করেছিলাম। কিন্তু মুকুর্জীকেও আমি খুব পছন্দ করিনি। সে ঠিক আমাদের মতো ছিল না। আমি কলকাতায় এসেও বাড়ীতে উঠতাম না। হোটেলে উঠতাম। ছোট হোটেলে। দু’চারদিন দু’চারবার বাড়ীতে আসতাম, দেখা ক’রে চলে যেতাম। কুইনিকে দেখার পর আমার আকর্ষণ বেড়েছিল, আমি তারপর থেকে বাড়ীতে আসতাম বেশি বেশি। দু’একবার থাকতেও ইচ্ছে হয়েছে কিন্তু থাকি নি মুকুর্জী আর মায়ের জন্যে। কুইনি যখন পাঁচ বছরের, তখন সেবার এসে তার সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়েছিল। সেবারই আমার মা মারা যায়। ডেথ বেড়ে মা আমার জন্যে একটু চিন্তিত হয়েছিল। মানি মুকুর্জীকে বলেছিল—হ্যারিসকে বাড়ীতে একখানা ঘরে থাকতে দিস আমি যেটায় থাকি। মানি মুকুর্জী রাজী হয়েছিল। আমি সেবার যাবার সময় ঠিক করে গিয়েছিলাম যে, এবার থেকে এসে হোটেলে আর উঠব না—এখানেই এসে উঠব। সব আকর্ষণ আমার পাঁচ বছরের কুইনির জন্যে। কিন্তু সেইবার গিয়েই ঘটে গেল আমার জীবনের সর্বনাশ!
এখন যে ঘটনায় তার জীবনটা এমন হয়ে গেল সেটা ঘটল সি-পিতে। একজন জংলী জোয়ান ছিল তার খুব অনুগত। তার সঙ্গে খুব দোস্তি ছিল তার। একসঙ্গে মদ খেত। যারা শিকার করতে যেত তাদের মধ্যে কারও ঝোঁক ছিল ট্রাইবাল গার্লসের উপর। এই বীরাই- বীরাই নাম ছিল জোয়ানটার, সে এনে দিত। বীরাইয়ের একটা কুকুর ছিল—ওদেশী কুকুর, কুকুরটা ছিল ভীষণ তেজী আর অত্যন্ত হিংস্র। হ্যারিসেরও একটা কুকুর ছিল, সে সেটাকে নিয়ে এসেছিল রাজাসাহেবের বাড়ী থেকে। একদিন দুটো কুকুরে ঝগড়া হয়ে মারামারি লেগে গেল। দুটো কুকুর একসঙ্গে বেশ থাকত। কিন্তু সেটা ছিল ওদের মেটিং সিজন।
চিরন্তন বিরোধের বীজের দুটি দল। একটি খাদ্য অন্যটি নারী। ঝগড়া লাগল তাই নিয়ে। জংলী কুকুরটা হঠাৎ হ্যারিসের কুকুর প্যাস্থারের গলায় কামড়ে ধরলে। সে কামড়ে ধরা আশ্চর্য হিংস্র ধরা। গলায় চারটে দাঁত ফুটিয়ে চেপে ধরে ক্রমাগত ঝাঁকি দিতে লাগল। হ্যারিস আর বীরা প্রথমটা দুজনেই দেখছিল ওদের লড়াই। প্রথমটা হ্যারিস বুঝতে পারেনি এই যুদ্ধের গুরুত্বটা কিন্তু যখন এমন ভাবে ঝাঁকি দিতে লাগল তখন সে ছুটে গেল ছাড়াবার জন্যে। কিন্তু নিষ্ঠুর হিংস্র বুনো কুকুরটা মার খেয়েও তা সহ্য করেও আঁকড়ে ধরে থাকল।
হ্যারিস বীরাকে চিৎকার করে বললে—ছাড়িয়ে দে বীরা ছাড়িয়ে দে!
বীরা হি হি ক’রে হাসছিল। সে বুঝতে পারেনি। কিংবা বুঝতে পেরেও ছাড়ায় নি। হ্যারিসের প্যাস্থার তখন নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। বীরা হাততালি দিচ্ছে। হ্যারিস আর সহ্য করতে পারে নি, সে ছুটে ঘরের ভিতর থেকে বন্দুক এনে তার অব্যর্থ নিশানায় ওই জংলী কুকুরটাকে গুলি করেছিল। মুহূর্তে বীরা চীৎকার করে ছুটে এসেছিল—আঁ, লড়াই করে মারলে আমার কুকুর-তু আমার কুকুরকে মারলি কেন? হ্যারিস বলেছিল—তোকে গুলি করব আমি। কিন্তু বীরা বন্দুকটা হঠাৎ আচমকা টেনে ছিনিয়ে নিয়ে ফেলে দিয়ে হ্যারিসকে আক্রমণ করেছিল। বলেছিল-তোকে এমনি করে মারব আমি। কিন্তু সেটা সম্ভবপর হয় নি। বীরার চেয়ে হ্যারিস শক্তিমান হোক বা না হোক সে প্যাঁচ জানত, বক্সিং জানত। সে তাকে ঘায়েল করেছিল। অবশ্য মার সেও খেয়েছিল যথেষ্ট। বীরা ঘায়েল হয়ে পড়েছিল, হ্যারিস উঠে দাঁড়িয়ে টলছিল। কিন্তু আক্রোশ তার তাতেও মেটেনি। হঠাৎ বন্দুকটা পড়েছিল নজরে। পড়েছিল সেটা। জ্ঞান তার ছিল না, সে বন্দুকটা কুড়িয়ে নিয়ে বীরার মাথায় বাঁট দিয়ে মেরেছিল একটা ঘা! কতটা জোরে মারছে তা তার খেয়াল হয়নি। বীরা তখন হামাগুড়ি দিয়ে উঠতে চেষ্টা করছিল এবং তাকে গাল দিচ্ছিল কুৎসিত ভাষায়। হ্যারিস বাঁটটা দিয়ে মারতেই মাথাটা ফেটে গেল। রক্ত বেরিয়ে এল গলগল ক’রে। বীরা লটকে পড়ে গেল। তখন তার খেয়াল হল এ সে করলে কি? মরে গেল লোকটা!
দুরন্ত আতঙ্কে সে সঙ্গে সঙ্গেই ঘর থেকে সামনে যা পেলে নিয়ে পালাল। কোথায় যাবে ঠিক ছিল না। মনে পড়েছিল কলকাতা। হেঁটেই সে রওনা দিয়েছিল। রেলস্টেশন—বনে বনে বিশ মাইল পথ। সেই পথটা সে সেই ক্ষতবিক্ষত দেহে পায়ে হেঁটে অতিক্রম করেছিল। শুধু তো পুলিশের ভয় নয়। বীরাজংলীর গ্রামে খবর গেলে তারা এসে তাকে তীর মেরে বিঁধে ফেলেই ছাড়বে না, টাঙি দিয়ে কুপিয়ে টুকরো টুকরো করে দেবে। তার বন্দুক দুটো ছিল। একটা রাইফেল, একটা দোনলা। কার্টিজও ছিল বাংলোতে কিন্তু তা দিয়ে কতক্ষণ রুখবে। স্টেশনে এসে ট্রেনে চেপে এসেছিল কলকাতা। কিন্তু মানির বাড়ীতে ওঠেনি। একখানা ঘর, মায়ের ঘরটা তার, মা দিয়ে গেছে, মানি রাজী হয়েছে দিতে তবুও ওঠেনি। ভয়ে ওঠেনি। মুকুর্জীর ভয়ে। এবং মানিও বোধহয় বিরক্ত হবে এসব শুনে—সেই ভয়ে।
উঠেছিল সে, যেসব বান্ধবীদের সে তার অরণ্য-স্বর্গে নিয়ে যেত, যারা সেখানে গিয়ে দ্বিগুণ উল্লাসে স্বচ্ছন্দচারিণী বনদেবী সেজে উল্লাস করত এবং কয়েক মাসে নোটের গোছা উপার্জন করে ও স্বাস্থ্য ফিরিয়ে কলকাতা ফিরত, তাদের মধ্যে যে অন্তরঙ্গতমা, তার বাড়ীতে। সেও তাকে আশ্রয় দিতে বিমুখ হয়নি। কিন্তু তাতেও নিষ্কৃতি পায়নি। পনের দিনের মধ্যে পুলিশ ঠিক এসে তাকে অ্যারেস্ট করেছিল।
তার দুর্ভাগ্য। বীরাজংলী সঙ্গে সঙ্গে মরেনি। দুদিন পর হাসপাতালে পুলিশের কাছে ডায়িং ডিক্লারেশন দিয়ে তবে মরেছিল। তাকে অজ্ঞান অবস্থায় দেখতে পেয়েছিল ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের লোক। তারা গ্রামে খবর দিয়ে গ্রামের লোকেদের এনে তাকে পাঠিয়েছিল দশ মাইল দুরের সাব-ডিভিশনাল টাউনে। সেখানেই বীরা ডায়িং ডিক্লারেশন দিয়েছিল, হ্যারিসসাহেব তাকে বন্দুকের কুঁদো দিয়ে মেরে মাথাটা ভেঙে দিয়েছে। কুকুরদুটোর বৃত্তান্তের সাক্ষী ছিল—কুকুরদুটোর ফটোগ্রাফ। বিচারে তার সাত বছর জেল হয়ে গেল।
এরই মধ্যে মুকুর্জী এবং মানি দুজনেই মারা গেছে। সে বিন্দুবিসর্গ জানত না। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে কলকাতায় ফিরেছিল হ্যারিস। আর কোথায় যাবে? মনে পড়েছিল—মানি তার মায়ের মৃত্যুশয্যায় মায়ের ঘরখানা তাকে দেবে বলেছে। সে গেলে, তার এইসব বৃত্তান্তের পর তারা খুশী হবে না সে জানত। মানির স্নেহ আছে। কিন্তু তবুও হয়তো খুশী হবে না। সে তো জানে, মানি মুকুর্জীকে কি রকম ভালবাসত!
মায়ের মৃত্যুর সময় সে দেড়মাস ছিল ওই বাড়ীতে, ওই সময়েই কুইনির সঙ্গে তার ভাব হয়েছিল, সে-সময় দু-চার দিন সে তার বন্ধু এবং বান্ধবীদের নিমন্ত্রণ করেছিল তার নিজের খরচে। কিন্তু—
তার কথাগুলো মনে পড়ছে সুলতা। হ্যারিস বলেছিল, মিস্তার মুকুর্জি ওয়াজ এ বেংগলী ক্রীশ্চান, এ সেলসম্যান ইন দি হোয়াটওয়ে লেডল কোম্পানী। হি ওলয়েজ সাফারড ফ্রম এন ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স ফ অ্যাংলো বয়েজ এ্যাণ্ড গার্লস। হি দিদ নত লাইক আওয়ার হুল্লাজ এ্যান্ড মেরিমেকিং। মাই সিস্তা মানি দো এ্যান এ্যাংলো গাল, কুদ নত জয়েন আস ফ হিম। শী লাভদ হিম ভেরি ডীপলি। অলসো মাই মাদা গ্রু এ্যাংরি উইথ মি। শী কার্সড মাই ফাদা।
Mr. Mookerjee was a Bengali Christian, a salesman in the Whiteaway Laidlaw Company. He always suffered from an inferiority complex for the Anglo boys and girls. He did not like our hullas and merry-making. My sister Mani though an Anglo girl could not join us for him. She loved him very deeply. Also my mother grew angry with me. She cursed my father.
অকুণ্ঠ স্বরে তার বাপের পরিচয়ও দিয়েছিল সে। বলেছিল, হ্যাঁ, বাবা তার লাইফ-এ সাকসেসফুল লোক ছিল না। চরিত্রেও সে অস্থির ছিল, তারই মত।
বলেছিল সে—My father was a pure Englishman. Came to India as a soldier. But was discharged for misconduct. Then he became a football trainer in an Anglo Indian football club. Then he became a sports goods dealer. There he lost everything. After that he got a job in the port police. There he met this Mr. Pedros, father of Mani. Pedros was a young man and my father was an old man of fifty-five or so. Mr. Pedros was an officer in an Indian firm-doing export import business. Pedros was their supervisor in the docks. Here they met and secretly organised a smuggling business together. You see, my father used to come to Pedros’ house everday and met my mother. Mr. Pedros died suddenly, leaving my mother and Mani. This house was Pedros’ own house. My father took advantage of this situation and induced my mother to marry him. When I was born -he again lost his job for misconduct, and lived on my mother, became a great drunkard. Then he died.
তার বাবা লোক ভাল ছিল না। সেও খুব ভালোমানুষ হতে পারেনি এটা সে মানে। তবু মানির উপর ভরসা করে কলকাতায় এসেছিল। এবং আশা করে এসেছিল এবার সে ভাললোক হতে চেষ্টা করবে। কুইনিকে স্নেহ করবে। কুইনিকে সে ইংরেজ এবং এ্যাংলো ইন্ডিয়ান সোসাইটিতে ইনট্রোডিউস করাবে। শরীরটা সেরে উঠলেই নতুন মানুষ হবে সে। তা যদি সম্ভবপর নাই হয়, শরীরটা সারলেই আবার সে যা-হয়-কিছু করবে। শিকারের নেশা তার এখনও আছে। বন্দুক তার গেছে, চেষ্টা করলে বন্দুক সে আবার পাবে। ইচ্ছে ছিল এবার জানোয়ার ধরার ব্যবসা সে করবে। না হয় সার্কাস পার্টিতে চলে যাবে। যা-হোক কিছু করবে। কিন্তু এলিয়ট রোডের বাড়িতে এসে সে-বাড়িতে অন্য লোকদের দেখে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। বাড়ীতে মানি নেই, মুকুর্জি নেই, তাদের ছোট্ট মেয়ে কুইনি নেই, তার জায়গায় একজন মিস্টার রাইট বাস করছে। তারা ভাড়া নিয়েছে গোটা বাড়ী। আশপাশের চেনা লোকেরা বলেছে তাকে যে, মুকুর্জি-মানি দুজনেই মরে গেছে। আগে মুকুর্জি, তারপর মানি। দুজনেরই থাইসিস হয়েছিল। মানির অসুখে সেবা করতে এসেছিল এই গোয়ানপাড়ার হিলডা পেড্রোস। মানির বাপ পেড্রোসের সে বোন হত। পেড্রোসের মা ছিল এই গোয়ানীদের মেয়ে। মানি চিঠি লিখেছিল তাকে। মানির মৃত্যুর পর এই হিলডা নিয়ে এসেছে কুইনিকে এখানে। এবং বাড়ীটা ভাড়া দিয়ে এসেছে এই রাইটকে।
কি করবে সে? তার আজ অর্থ নেই, আশ্রয় নেই। তাছাড়া ‘কুইনি’ মানির মেয়ে, তার ভাগ্নী, শেষে সে এই গোয়ানদের গ্রামে এসে একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে, অসভ্য হয়ে যাবে! তাই সে এসেছে এখানে। সে চায় কুইনিকে নিয়ে সে এলিয়ট রোডের বাড়ীতে সংসার পাতবে। তার আর কে আছে? কুইনিই তার সব হবে। তাকে মানুষ করবে।
—ভেরী সুইট গাল। য়ু সী! Very sweet girl, you see.
কিন্তু হিলডা তাকে আমল তো দেয়ই নি, তাকে নানান কটু কথা বলেছে। বলে, মানি তাকেই কুইনির গার্জেন করে গেছে। যা করবার সেই করবে। সে মিদনাপুরে কুইনিকে ইস্কুলে ভর্তি করে দেবে, নতুন সেসন আরম্ভ হলে। কিন্তু সেসব মিথ্যে কথা। কিচ্ছু করবে না। আর সে গার্জেন কি করে হবে সে থাকতে? সে কুইনির মায়ের ভাই, এক মায়ের পেটের ভাই-বোন, না হল এক বাপের! হিলডার এটা নিজের জায়গা। সে এখানে অসহায়। কাল সারাদিন ধরে খারাপ কথা শুনে শেষে রয়বাবুর নাম শুনে সে এখানে এসেছে। শুনেছে সে যে গোয়ানপাড়ার প্রত্যেকে রয়বাবুকে মানে। হিলডাও মানে, খাতির করে।
—আপনি রয়বাবু গোয়ানপাড়া রেন্টফ্রি করে দিয়েছে। এখানকার লোকের ভি বহুৎ রাইট দিলে। য়ু হ্যাভ এ ফাইন সেন্স অব জাস্টিস—You have a fine sense of justice, রয়বাবু, য়ু প্লিজ হেল্প মি, তেল দ্যাত হিলদা তু গিভ কুইনি তু মি। You please help me, tell that Hilda to give Quinee to me.
সে তাকে পড়াবে। সত্যকারের ফাইন লেডী হবে সে।
আমি তার কাহিনী শুনে বিস্মিত হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবছিলাম, ওই লোকটির কথা। কুইনিকেও মনে পড়ছিল। কথাবার্তাগুলিও মনে পড়ছিল। নমস্কার স্যার! কিছুক্ষণের জন্য রায়বাড়ীর কাহিনী—বীরেশ্বর রায়, রত্নেশ্বর রায়, অতুলেশ্বর, মেজদিকে নিয়ে যে-বিচিত্র চিন্তা জেগেছিল, তাও ভুলে গিয়েছিলাম। বিস্ময়কর বিচিত্র জীবন!
লোকটাই আমাকে সচেতন করে তুলেছিল—রয়বাবু!
ঘোরটা ভেঙে গিয়েছিল।
আমি তাকে বলেছিলাম-ইয়েস মিস্টার হ্যারিস, কাল আমি সকালবেলা হিলডাকে ডাকব। কুইনিকেও সঙ্গে আনতে বলব। তাদের কাছে এ বিষয়ে তাদের কি বলবার আছে জিজ্ঞাসা করব। তারপর তোমাকে উত্তর দেব। তার আগে কিছু তো বলতে পারব না।
হ্যারিস এইটুকুতে খুশী হয়েছিল। বলেছিল, রয়বাবু, আই নিড ইট। তুমি এই বলবে আমি জানতাম। নিশ্চয় তুমি শুনবে। তবে তুমি বিচার করে দেখো, সে সঙ্গত কথা বলছে কিনা! হয়তো বলবে, আমি মার্ডারার। হয়তো বলবে, আমি বদমাস। আমি ওই শিকারের সময় গার্লস নিয়ে যেতাম, আমি পাজী লোক, কিন্তু দেখ, সে করতাম বাধ্য হয়ে আমার প্রফেশনের সুবিধের জন্যে, আর সে মেয়েরাও ছিল প্রফেশনাল। কিন্তু আমি তো ভদ্রলোক।
কথাগুলো আমাকে আর একটা দিক সম্বন্ধে সচেতন করে দিয়েছিল সুলতা, আমি তাকে কথায় বাধা দিয়ে বলেছিলাম, সেসব কাল শুনব। আজ আর নয়। এগারটা বাজছে। তুমি এস। কিন্তু তুমি রয়েছ কোথায়? হিলডার বাড়ীতে?
—না। সে থাকতে অবশ্য বলেছিল। কিন্তু তা আমি থাকিনি। হিলডা বড় রাফ রুড তাছাড়া ওদের ঘরদোর ভাল নয়। হিলডাই আমাকে বলেছিল, চার্চের পাশে একখানা ঘর আছে সেখানে থাকতে। মিদনাপুর থেকে পাদ্রী এসে থাকে। আমি তাও থাকিনি। আমি অন্য একজনের বাড়ীতে রয়েছি। তাকে টাকা দিয়েছি—ক্যাশ ফাইভ রূপিজ। সেখানে থাকছি।
লোকটা চলে গেলে কিছুক্ষণ আমি ওর কথাই ভেবেছিলাম। বিচিত্র জীবন; পঞ্চান্ন বছরের বৃদ্ধ ওর বাপ, আর্মি থেকে ডিসচার্জড হয়ে ফুটবল-ট্রেনার, তারপর দোকান। তারপর পোর্ট-পুলিশে ঢুকে স্মাগলিং। ছেলে টেনিস ক্লাবে বয়, সেখান থেকে উড়িষ্যায়, নেটিভ স্টেটে গিয়ে শিকারী। খুন। জেল। জাতটাই বিচিত্র।
খেয়েদেয়ে শুয়ে ঘুম আসেনি, ফিরে এসেছিলাম রায়বংশের কথায়। সেদিনের আজকের কথায়। ছবি আঁকার কল্পনা নিয়েই শুয়ে জেগে ছাদের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। হঠাৎ কল্পনা একটা এল, খুব উৎসাহিত হয়ে উঠলাম।
আঁকব, ১৮৫৭ সালে কুইনস ডিক্লারেশনের সময়, ডিক্লারেশন পড়ছেন কলকাতায় লর্ড ক্যানিং। মেদিনীপুরে পড়ছেন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট একটা প্যান্ডেলের তলায়। প্যান্ডেল নয় সেটা, ছাদই হবে। ছাদের তলায় মোটা মোটা সারিবন্দী থাম। থামের পায়াগুলো মোটা পাথরের, সেগুলো এক-একটা জমিদারী এস্টেট। আর থামগুলো শক্ত পাথরে খোদাই মানুষের মূর্তি। তাঁরা জমিদার, কারও টাইটেল রাজা, কারও মহারাজা, কারও রায়বাহাদুর, কারও রায়সাহেব, কারও বা খেতাব নেই। আর অগণিত ভীতিবিহ্বল মানুষ। তারা চাষী, তারা গৃহস্থ, তারা সাধারণ মানুষ। চারিদিক ঘিরে থাকবে পুলিশ, মিলিটারী। ছাদটার মাথায় উড়ছে ইউনিয়ন জ্যাক।
আর একটা আঁকব- ১৯৩০ সাল। সেটাতে সেই ছাদ, সেই পুলিশের বেষ্টনী, মিলিটারীর পাহারা। এবং চাষীগৃহস্থেরা বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়েছে, চোখে বিদ্রোহী দৃষ্টি। আর ওই থামগুলোর পাথরের মানুষ জেগে উঠেছে। তার মধ্যে কীর্তিহাটে যে-স্তম্ভটা বীরেশ্বর রায়ের মূর্তি ছিল, সেটা ফেটে গেছে, তা থেকে বের হচ্ছে অতুলেশ্বর, তার হাতে তেরঙ্গা ঝাণ্ডা। আর পাশে দাঁড়িয়ে মেজদি দিচ্ছেন আশীর্বাদ, অর্চনা বাজাচ্ছে শাঁখ।
অনেক রাত্রি পর্যন্ত ঘুমোইনি। মনে হয়েছিল চীৎকার করি আনন্দে। হ্যাঁ, পেয়েছি। পেয়েছি। এই আইডিয়া নিয়েই দুখানা ছবি আঁকব আমি। এই আমার এই ছবির একজিবিশনের সূচনা বীজ।
অনেক রাত্রে সেদিন শুয়েছিলাম।
রাত্রি শেষ হয়েছে। বাইরে মহানগরীর বর্তমান জেগেছে। বিরাট কর্মকাণ্ডের চাকাটা সশব্দে চলতে শুরু করেছে। গঙ্গার বুকে জাহাজে স্টীমারে ভোঁ বাজছে। মিলের পর মিলে সাড়ে পাঁচটার সিটি সাইরেন-ভোঁ বাজছে। গাড়ির চলাচলের শব্দ শোনা যাচ্ছে। পাখির শব্দ হারিয়ে গেছে। তাকে ছাপিয়ে উঠছে মানুষের সাড়া।
তাকে উপেক্ষা ক’রেই সুরেশ্বর বলে চলল—সুলতা, পরের দিন সকাল –সে দিনটি ছিল ১৯৩৭ সালের জানুয়ারী মাসের ২৬শে। ১৯৩০ সাল থেকে ২৬শে জানুয়ারী ভারতবর্ষের ইতিহাসে চিহ্নিত হয়েছে। আজ সে পূর্ণ মূল্য পেয়ে সগৌরবে পৃথিবীর ইতিহাসে চিহ্নিত। কিন্তু সেদিন ১৯৩৭ সাল ভারতবর্ষের মানুষের বুকে ওর স্থান ছিল ভাবী জননীর প্রত্যাশিত দিনটির মত।
আমি ওই দিন—ওই দেখ ওই ছবিখানা আরম্ভ করেছিলাম সকালে উঠেই। আমার মনেই ছিল না হ্যারিসের কথা। সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছিলাম। প্রথমে উঠে ক্যানভাস বের করে ইজেলের উপর চাপাচ্ছি, মনে পড়ল আজ ২৬শে জানুয়ারী। একখানা পতাকা টাঙাবার ইচ্ছে হয়েছিল। কিন্তু পতাকা কোথায় পাব? হঠাৎ মনে হয়েছিল এ তো আর বীরেশ্বর রায়, রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায়ের সম্পদ-গৌরব-ঝলমল রায়বাড়ী নয়। এ অতুলেশ্বরের রায়বাড়ী। জীর্ণ ফাটল ধরা শ্যাওলা-পড়া পলেস্তরা-খসা রায়বাড়ী।
আজ নতুন কালের পতাকা থাকবে না? নিশ্চয় থাকবে। অতুল পিস্তলগুলি যোগাড় করেছিল আর পতাকা যোগাড় করেনি? পিস্তলটা মেজদি বের ক’রে দিয়েছেন, আমি গোপনে কার্টিজগুলো ফেলে দিয়েছি। রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায়ের যে ঘরটায় মহারানী ভিক্টোরিয়ার বড় অয়েল পেন্টিং টাঙানো ছিল সেই ঘরটাই অতুলেশ্বর ইংরেজরাজত্ব উচ্ছেদের লড়াইয়ে অস্ত্রাগার করেছিল। এ বাড়ীতে জাতীয় পতাকার অভাব হবে?
অর্চনাকে ডেকে পাঠালাম আমি। অর্চনা এসে বললে-ডেকেছ সুরোদা?
তার মুখের দিকে তাকিয়ে আমি চমকে উঠলাম। অর্চনার চোখ দুটো লাল হয়ে উঠেছে। অস্বাভাবিক রকমের লাল। গৌরবর্ণ মুখখানাও যেন রাঙা দেখাচ্ছে। মনে হল জ্বরটর হয়েছে। বললাম—তোর মুখ-চোখ এমন কেন রে?
সে বললে-ও কিছু না।
—কিছু না মানে? জ্বরটর হয়েছে নাকি?
–না। এখন বল কি বলছ?
—দেখি—তোর কপালের তাপ দেখি।
—না—দেখতে হবে না। কাল রাত্রে ঘুম হয়নি।
এবার ওর চোখে জল দেখতে পেলাম। এবার বুঝলাম সারারাত কেঁদেছে মেয়েটা। আমি বললাম—তুই মিথ্যে এমন ক’রে কাঁদিস নে। মেজদি বা অতুলের জন্যে কাঁদতে নেই।
এবার দরদর করে জল গড়িয়ে এল চোখ থেকে। তাড়াতাড়ি চোখ মুছে নিজেকে সামলাবার চেষ্টা ক’রে বললে—না, তাদের জন্যেও কাঁদিনি সুরোদা। তুমি বল কি বলছ।
আমি বললাম—না। বল তুই আগে কি হয়েছে।
এবার সে বললে—আমাকে বলির ব্যবস্থা হয়েছে সুরোদা। তাই কেঁদে নিচ্ছি।
—তার মানে?
—বাবা আমার বিয়ের সম্বন্ধ ক’রে এসেছে—একজন পুলিশ সাবইন্সপেক্টারের সঙ্গে। আমার মামার শালার ছেলে। তার স্ত্রী মারা গেছে। মামা সম্বন্ধ ক’রে দিয়েছে। আমি শেষে
কথা শেষ করতে পারলে না অর্চনা—আবার ঝরঝর করে কেঁদে ফেললে। আমি কয়েক মুহূর্ত স্তম্ভিত হয়ে রইলাম সুলতা; তারপর বললাম—তুই ভাবিস নে-এ বিয়ে হতে আমি দেব না। আমি জগদীশকাকার হাতে পায়ে ধরব—বলব- অর্চির বিয়ের ভার আমার। আমি পাত্র দেখে যা খরচ করতে হয় ক’রে ওর বিয়ে দেব। ভাবিস নে।
অর্চনা চোখ মুছে হাসল। সে হাসির মানে আলাদা—জাত আলাদা। তার মানে একটা নয় অনেকগুলো। তাতে যত ব্যঙ্গ তত ক্ষোভ। সে হাসি যত ধারালো তত বাঁকা। বললে—যেয়ো, বাবা অপমান করবে। সম্বন্ধ পাকা ক’রে এসেছে। দিন পর্যন্ত একরকম স্থির। ফাল্গুনের শেষে। টাকা নেবে না। সরকারী চাকরে। মাকে কাল আমি বলেছিলাম—বিয়ে আমি করব না। জোর করলে বিষ খাব। বাবা ঠাস করে এক চড় মেরেছে আমার গালে! ও থাক। সে যা করবার আমি করব। এখন কি বলছ বল!
—অর্চনা? আমি তার মুখ-চোখে একটা নিষ্ঠুর সঙ্কল্পের আভাস দেখতে পেয়েছিলাম।
—আঃ! বল না কি বলছ!
তার হাত চেপে ধরে বললাম—বল্ তুই বিষ খাবি নে! তুই বিষ খাবি! আমি বুঝেছি।
হেসে ফেলে সে বললে-খাব না। হল তো!
—তবে? তবে তুই কি করবি?
—সে আমি বলব না।
—অৰ্চনা?
একটু চুপ ক’রে থেকে অর্চনা বললে—আবারও আমি বলব সুরোদা। তাতেও যদি না মানে আমি পুলিশকে চিঠি লিখব যে রায়বাড়ীর অর্চনা ব’লে মেয়েটা অতুলকার সঙ্গে এইসব কাজ করেছে। তাহ’লে আমাকে ধ’রে নিয়ে যাবে। পুলিশ দারোগাসাহেবও আমাকে বিয়ে করতে রাজী হবে না!
আমি চমকে উঠেছিলাম। তাকে অবিশ্বাস করতে পারি নি। আমি তার হাতখানা চেপে ধ’রে বলেছিলাম—না। তা করবি নে।
—তা হ’লে কি করব বলতে পার?
আমি উত্তর দিতে পারি নি। সে হেসে বলেছিল-বল? বল কি করব?
আমি ভেবেই বলেছিলাম—আমি জগদীশকাকাকে ডেকে বা তার কাছে গিয়ে সব কথা গোপনে বলব। এবং বিয়ের ভার আমি নেব। নিশ্চিত থাক। সব শুনে জগদীশকাকা কখনও জেদ করবে না!
একটু চুপ ক’রে থেকে সে বলেছিল—বেশ তাই হ’ল। এখন কি বলছ বল। আমি এখন ঠাকুরবাড়ী যাব। মেজদি নেই। একবার গিয়ে দাঁড়াতে হবে। না হলে পুরুতরা পুজুরীরা যা মন তাই নমো নমো করে পুজো সেরে পালাবে।
—সে করিস। কিন্তু এখুনি যে আমার একটা ফ্ল্যাগ চাই।
—ফ্লাগ?
—হ্যাঁ, কংগ্রেস ফ্ল্যাগ। আজ ২৬শে জানুয়ারী।
—ফ্ল্যাগ তুলবে?
—হ্যাঁ।
—না, তুলো না। বাড়ীতে স্পাই রয়েছে। ঝোঁকের মাথায় কিছু করতে গিয়ে আর মিছিমিছি জট পাকিয়ো না।
অবাক হয়ে গিয়েছিলাম আমি—বাড়ীতে স্পাই রয়েছে? কি বলছিস রে? কে?
—অবাক হচ্ছ কেন? কল্যাণদাকে চেনো না? এই মামলাটা যতদিন চলছে—ততদিন ওর সঙ্গে থানার বাবুদের চিঠি চালাচালি হচ্ছে। ওর রাগ তোমার ওপর। তোমাকে জড়াবার চেষ্টার অন্ত নেই। মেজজ্যাঠাকে তো জানতে। তার নিজের হাতের তৈরী সিপায়ের ঘোড়ার মত বাপের বেটা। সুষি আমাকে বলেছে। সুষমা ওর নিজের বোন, সে মিথ্যে কথা বলবে না। আবার বলতেও পারি না সেও দাদার সাগরেদ কিনা। আমাকে বার বার বলেছে—মেজদির ঘরে কি অতুলকার ঘরে আর কিছু আছে তো ফেলে দে অর্চি। আমি বললাম-আমি কি করে জানব সুষি? তা বললে—তুই তো মেজদির সঙ্গে ফিরতিস—বাঘের সঙ্গে ফেউয়ের মত। তাই বলছি। আর সুরোদার কাছে এমন ক’রে যাসনে। দাদা বলছিল —সুষি, বিবিমহলের দিকে খবরদার যাবি নে, সুরেশ্বরদার কাছে। ওর ওপর পুলিস নজর রাখছে। মেজজ্যাঠা ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ছিল জান তো? বোর্ড এ জেলায় চলে নি। তবুও আঁকড়ে ধরেছিল—ছাড়েনি। কত বলেছে লোকে—কিন্তু তবু ছাড়েনি। মেজজ্যাঠার মৃত্যুর পর থেকে কল্যাণ সেটা ধরেছে। আজ সকালবেলা থেকে ছাদের ওপর ঘুরছে। কি? না, কার বাড়ীতে কোথায় ফ্ল্যাগ উঠেছে দেখছে। ওসব যাক। আমার কথা শোন। তোমার কথা আমি শুনব—যদি তুমি আমার কথা শোন। আমি চললাম সুরোদা, বাবা খুঁজবে আমাকে!
বলে আর দাঁড়াল না সে। চলে গেল। আমার মনের ক্ষোভ বল ক্ষোভ-ক্রোধ বল ক্রোধ—অসহায় হিংসা বল হিংসা-বেড়ে গিয়েছিল সুলতা। আমি কোনমতে সান্ত্বনা পাই নি। ফ্ল্যাগ ওঠাব না? ফ্ল্যাগ নেই কিন্তু আমি ছবি আঁকি, রঙ দিয়ে কাপড়ের ফালির উপর ছবি আঁকতে কতক্ষণ লাগবে আমার?
এরই মধ্যে ভুলে গিয়েছিলাম সব। কিছুক্ষণ পর ছবি আঁকতে শুরু করেছিলাম। কাপড়ে রঙ করে ফ্ল্যাগ তৈরী করে বিবিমহলের ছাদের উপর তোলা হয় নি-সম্ভবতঃ অর্চনার কথায় আমি ভয়ই পেয়েছিলাম। কারণ অর্চনার কথাটাই আমার কাছে বড় হয়ে উঠেছিল। অৰ্চনা বলেছে—“আমার কথা মানলে তোমার কথা মানব।” আজ মনে মনে খতিয়ে দেখে বার বার নিজেকেই জিজ্ঞাসা করেছি—তাই কি সত্যিই করত? করতে পারত? আজ আমার মন বলে পারত না। কখনোই পারত না। বিপ্লবীরাও তা পারে না। চট্টগ্রামের অনন্ত সিং নিজে এসে কলকাতার আই বি আপিসে ধরা দিয়েছিলেন-তার কারণ অন্য। তখন দল ধরা পড়েছে। আর তার সংসারের উপর নিষ্ঠুর নির্যাতন হচ্ছে। এবং তখন তিনি ভেবেছিলেন তাঁর ‘মিশন’ শেষ হয়েছে। তিনদিনের জন্যে চট্টগ্রামে ইউনিয়ন জ্যাকের জায়গায় তেরঙ্গা ঝাণ্ডা উড়িয়ে, ভারতবর্ষের একখানা শহরকেও স্বাধীন করে স্বাধীনতার যে পত্তন করে গেলেন তাতেই বীজ পোঁতা হল।
কিছুদিন আগে পড়েছি সুলতা, কোথায় কোন বৌদ্ধমঠে নাকি একটি পাত্রের মধ্যে হাজার বছরের পুরনো পদ্মবীজ ছিল। সেই বীজটা মঠের ধারে জলাশয়ে পড়ে তা থেকে গাছ হয়েছে এবং ফুলও ধরেছে সে গাছে।
সুতরাং বিচার করে দেখেই বলছি—সেদিন আমার মনের মধ্যে ভয়ই ছিল। আবার লজ্জাও ছিল। মনে হয়েছিল, আমি ইংলিশম্যান স্টেটসম্যানের যোগেশ্বর রায়ের ছেলে, আমি নিজে তিরিশ সালে জেল থেকে ফিরে বিদায় সত্যাগ্রহ বলে চিঠি লিখে স্টেটসম্যানে ছাপিয়ে পিছিয়ে এসেছি, আজ আর মুক্ত রণক্ষেত্রে এগিয়ে যাবার অধিকারই নেই। হয়তো নিজেই এমন দুর্বল যে ঝোঁকের মাথায় করে ফেলে ধরা পড়ে নির্যাতন সইতে না পেরে সর্বনাশ করে ফেলব।
ছবিই আঁকছিলাম ফ্ল্যাগ তোলার বদলে। তার মধ্যেই থাকবে ফ্ল্যাগ। বীরেশ্বর রায়রূপী ১৮৫৭ সালের স্তম্ভটা ফেটে গিয়ে ভেঙে পড়ছে, তারই মধ্যে থেকে অতুল বের হচ্ছে ফ্ল্যাগ হাতে। পাথরের থামটার পায়া কীর্তিহাটের জমিদারী ফেটে চৌচির হয়ে টুকরো টুকরো পাথরের একটা স্তূপে পরিণত হয়েছে।
এরই মধ্যে বেলা তখন নটা বেজে গেছে। আমি ইজেল পেতেছি কাঁসাইয়ের ধারের বারান্দাটায়। ওপারে সিদ্ধপীঠের জঙ্গল। জঙ্গলটার পশ্চিম প্রান্তে আমার সামনের দিকে অনেকটা পশ্চিমে গোয়ানপাড়া, ডাক শুনলাম—Sir, Roy Babu.
আমি তুলিটা চালাতে চালাতেই ডাকটা শুনলাম। তুলি তুলে তার দিকে তাকালাম। দেখলাম ওপারে দাঁড়িয়ে কালকের সেই হ্যারিস।
কি জানি কেন, মুহূর্তে একটা কঠিন ক্রোধে আমি যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলাম। মনে হয়েছিল লোকটা আমাকে একটি শুভ কাজে বাধা দিলে। আরও বেশী রাগ হয়েছিল লোকটা অ্যাংলোইন্ডিয়ান বলে। এরা এদেশের মানুষ হয়েও এদেশের শত্রু। অন্ধবিশ্বাসী মানুষের মতই বিশ্বাস হয়েছিল সেই মুহূর্তে সুলতা যে, যে মুহূর্তে কীর্তিহাটের জমিদারস্তম্ভ ফাটিয়ে অতুলেশ্বর বের হচ্ছে—এই ছবিটি আঁকতে যাচ্ছি—সেই মুহূর্তে ওই লোকটার এই পিছন ডাকা যেন ইঙ্গিতময়।
তুলিটা ফেলে আমি রূঢ়কণ্ঠে বলেছিলাম—আমার এখন সময় হবে না মিঃ হ্যারিস! সন্ধ্যেবেলা দেখব। এখন যাও।
সে কিন্তু ছাড়েনি। বলেছিল—কিন্তু তুমি আমাকে কাল কথা দিলে রয়-বাবু! তুমি নিশ্চয় সাধারণ লোক নও। আশা করি কথা তুমি রাখবে। তা না হলে আমি নিশ্চয় চলে যেতাম। দেয়ার ইজ কোর্ট।
আমি প্রাণপণে আমার রাগ চাপবার চেষ্টা করছিলাম। তবু ঠিক তা চাপতে পারছিলাম না। তার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলাম।
সে বলেই চলেছিল—ইউ আ এ বিগ জমিন্ডার—গত এ বিগ হাউস, সন অব অ্যান অ্যারিস্টোক্র্যাটিক ফ্যামিলি-ইউ শুড অ্যান্ড মাস্ট কীপ ইয়ো ওয়ার্ডস।
You are a big Zaminder, got a big house, son of an aristocratic family- you should and must keep your words.
কথাবার্তা শুনে মনে হ’ল লোকটা সকালেই বোধহয় মদ্যপান করেছে। পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে একটু একটু দুলছে।
কঠিন ক্ষোভ হয়েছিল। কিন্তু ওকে চীৎকার ক’রে খেদিয়ে দিয়ে নিজেকে ছোট করতে পারি নি। লোকটা এখান থেকে চলে গিয়ে পথে পথে গাল দিতে দিতে যাবে। আমি বলেছিলাম—দাঁড়াও, আমি যাচ্ছি। গোয়ানপাড়া গিয়ে এখুনি হিলডা কি বলে শুনে আসব।
হ্যারিস বলেছিল—তুমি যাবে রয়বাবু? হোয়াই? হিলডাকে ডাক তুমি!
—না। তাতে অনেকক্ষণ সময় নেবে।
আমার ইচ্ছেও হয় নি ওকে ঘরে ঢুকতে দিতে। জামাটা গায়ে দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিলাম। সঙ্গে গিয়েছিল ডিক্রুজ। ছুটে আগে চলে গিয়েছিল গোমেশ পাড়ায় খবর দিতে।
আমি জানতাম না সুলতা, যে আমি ওই হ্যারিসের ডাকে যাচ্ছি না। যাচ্ছি নিয়তির আকর্ষণে। তা ছাড়া আর কি বলব আমি বুঝতে পারি না। সেদিন থেকে আজও পর্যন্ত না।
সুলতা বিস্মিত হয়ে তার মুখের দিকে তাকালে। কিন্তু প্রশ্ন কিছু করলে না।
সুরেশ্বর বললে—আমি গোয়ানপাড়ায় যেতেই পাড়ায় একটা সোরগোল পড়ে গিয়েছিল। হিলডা আমাকে সম্বর্ধনা করবার জন্য বিব্রত হয়ে উঠে হাঁকডাক শুরু করে এমন একটা কাণ্ড করেছিল যে আমি লজ্জিত হয়েছিলাম। বারণ করলেও সে শোনে নি। চেয়ার বের করে আনতে গিয়ে বেচারী পড়ে গিয়ে আঘাত লাগিয়েছিল পায়ে। ত্রাণ করেছিল কুইনি এসে।
কুইনি ওদের চার্চের পাশের ঘরে পাঠশালায় ছেলেদের পড়াচ্ছিল। এখানে আসবার আগে পর্যন্ত সে কলকাতায় ইস্কুলে ক্লাস নাইনে পড়ত। এখানে এসে ছেলেদের নিয়ে একটা পাঠশালা খুলেছে। সে পড়ায় তাদের। কুইনিকে দেখে চিনতেও সেদিন কষ্ট হয়েছিল। সেদিন সে ফ্রক পড়ে নি। পরেছিল শাড়ী। তাতে অনেকটা বড় দেখাচ্ছিল। সুন্দর একটি বাঙালীর মেয়ে। মাজা রঙ, চোখে যেন ইউরোপের নীলের আভাস। চুলে ঈষৎ পিঙ্গলাভা। রুখু চুলের বেণী পিঠে ঝুলিয়ে সে এসে হিলডাকে বলেছিল- বস তুমি। ব্যস্ত হয়ো না। রায়বাবু এসেছেন—উনি দাঁড়াবেন একটু। তাতে কি হয়েছে? আমরা তো খবর জানি না! তারপর চেয়ারখানা ভাল করে পেতে দিয়ে বলেছিল-বসুন স্যার।
হিলডা বলেছিল—আপনে আসবেন বাবু খবর না মিললে কি করবে হামরা। আপনে গোটা গোয়ানপাড়া লখরাজ করে দিলে-আপনে জমিদার—আপনে আসবেন —
বাধা দিয়ে আমি বলেছিলাম—আমি খুব জরুরী কাজে এসেছি হিলডা। মিঃ হ্যারিস—! হ্যালো মিস্টার হ্যারিস!
হ্যারিসকে দেখতে পাইনি। সে পিছন পিছন আসছিল, কোথায় গেল বুঝতে পারলাম না। কিন্তু হিলডা হ্যারিসের নাম শুনে যেন ক্ষেপে গেল। চীৎকার ক’রে উঠল—হ্যারিস—উ বদমাস—বজ্জাত-খুনী আদমীঠো আপকে পাশ গিয়েছে? হারামী কি বাচ্চা হারামী, খুনীকে লেড়কা খুনী! হারামীর বাবা—হামার ভাই পিড্রোস—ওই হ্যারিসের বাপকে লিয়ে জান হারালে বাবুসাব। উ হারামী কলকাত্তা সে ফিরিঙ্গী ছোক্রী লোককে লিয়ে গিয়ে বড়ালোক বদমাস লোকের কাছে বেচত—উ কুইনিকে নিতে আসছে। হারামী বেচে দিবে কুইনিকে
হঠাৎ ওপাশ থেকে উচ্চতর কণ্ঠে কুৎসিত ভাষায় হ্যারিসের সাড়া পেয়ে তাকালাম ফিরে। রুমালে মুখ মুছতে মুছতে সেও গাল দিচ্ছে—ইয়ু বিচ্—
সে অশ্রাব্য ভাষা। তেমনি কর্কশ উচ্চকণ্ঠ। বুঝতে পারলাম, যা মদ সে খেয়েছিল, তাতে ঠিক এইভাবে ঝগড়া করবার মতো মনের বল পায় নি হ্যারিস, সে আমার পিছনে আসতে আসতে সম্ভবতঃ তার পাঁচ টাকায় ভাড়াকরা আস্তানাতে গিয়ে আরও মদ গিলে ফিরছে, এই মুহূর্তে।
আমি ধমক দিয়ে হ্যারিসকে বলেছিলাম-হ্যারিস! চুপ কর তুমি!
হ্যারিস থামে নি—চীৎকার করে উঠেছিল—দ্যাট বিচ ইজ লাইং—
কুইনি চুপ ক’রে দাঁড়িয়েছিল এতক্ষণ, এবার সে ইংরিজীতে হ্যারিসকে বললে—শী ইজ নট লাইং। ইট ইজ ফ্যাক্ট!
হ্যারিস কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে গেল। তারপর হঠাৎ আবার চীৎকার করে বলে উঠল- ইউ ডটার অব এ ব্ল্যাক নিগার-হাউ ডেয়ার ইউ সে সো—
—মিস্টার হ্যারিস!
কুইনির কণ্ঠস্বরকে চাপা দিয়ে হ্যারিস চীৎকার করেই চলেছিল। আমার আর সহ্য হয় নি—আমি ডিক্রুজ আর গোমেশকে বলেছিলাম—তোমরা দাঁড়িয়ে আছ আর ও লোকটা এইভাবে গালাগাল দিচ্ছে? বলে আমি নিজেই উঠে গিয়ে তার কলারটা চেপে ধরে ঝাঁকি দিয়ে বলেছিলাম—উইল ইউ স্টপ? অর—।
লোকটার দৃষ্টি আমার দিকে ছিল না—ছিল আমার পিছনে এবং তার চারিপাশে গোয়ান পুরুষেরা এগিয়ে আসছিল তার দিকে!
সে এবার চুপ করে গিয়েছিল। নেশার মধ্যেও তার বোধহয় জ্ঞান উঁকি মেরেছিল। সে বলেছিল—অল্ রাইট বাবু; অলরাইট। লীভ মী প্লিজ। আই প্রমিস টু কীপ কোয়ায়েট!
তাকে ছেড়ে দিয়ে আমি ব্যাপারটা সংক্ষেপ করবার জন্য কুইনিকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম —কুইনি, এ বলে এ তোমার মামা। সে তোমাকে নিয়ে যেতে চায় কলকাতা।
কুইনি বলেছিল—না। আমি ওর সঙ্গে যাব না।
আমি বলেছিলাম-বেশ। কিন্তু ও বলছে-তোমাদের যে বাড়ী আছে এলিয়ট রোডে, সে বাড়ীর একখানা ঘর তোমার মায়ের মা ওকে দিয়ে গিয়েছিল। সেই ঘরখানা সে চাচ্ছে। হিলডা গোটা বাড়ীটা ভাড়া দিয়ে এসেছে।
হিলডা এবার আবার রাগে ফেটে পড়ল।
বলতে বলতে সুরেশ্বর যেন চঞ্চল হয়ে উঠল। চুপ করে গেল কিছুক্ষণের জন্য। তারপর মাথা হেঁট করে তার সামনের লম্বা রুক্ষ চুল ডান হাতের মুঠোয় চেপে ধরে বলে উঠল—ওঃ!
সুলতা বুঝতে পারলে এই স্মৃতি তার কাছে নিষ্ঠুর পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছে।
পূর্ণ সত্যের উপর দাঁড়িয়ে জীবনের জবানবন্দী দেওয়া তো সহজ নয়। ভিতর থেকে গলা চেপে ধরে এমনি করে। সে চুপ করে রইল। বাইরে দিনের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। তার ইচ্ছে হল বলে, থাক সুরেশ্বর, আজ এইখানেই থাক। বরং আজ সন্ধ্যেয় এসে শুনে যাব। কিন্তু তার পুর্বেই সুরেশ্বর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে, সেদিনের ঘটনাগুলো আমার কাছে শুধু স্মৃতি নয়, আমার কাছে ছবির মত প্রত্যক্ষ হয়ে ভেসে ওঠে।
সে-ছবি আমি এঁকেছি। ওই দেখ ছবিটা। সে উঠে গিয়ে একখানা ছবির সামনে দাঁড়াল। হাত বাড়িয়ে দেখালে—এইখানা। সেখানাও সুরেশ্বরের আঁকা বড় ছবির মধ্যে একখানা।
সুলতা দেখলে, একটা টালি দিয়ে ছাওয়ানো ঘর। ঘরটার মাথায় একটা ক্রশ। দেখলেই বুঝতে পারা যায়—একটি চার্চ। তার সামনে একটি জনতা। পিছনে মাটির ঘরের খড়ের চালের আভাস, তার পিছনে দিগন্তের গাছপালা।
জনতার মধ্যে চেয়ারে বসে সুরেশ্বর, তার চোখ বিস্ফারিত। বিস্ময়-আতঙ্ক-লজ্জা তার মধ্যে ফুটে রয়েছে। তার পাশে একটি বৃদ্ধা মেয়ে, পরনে ঢিলেঢালা ফ্রক অথবা সেমিজ। মুখখানা শতরেখায় রেখাঙ্কিত, চোখে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি, একটা হাত বাড়িয়ে আছে সে। তার পাশে আধুনিক কালের বাঙালী মেয়ের মত ফেরতা দিয়ে কাপড়-পরা একটি সুশ্রী তরুণী মেয়ে বিবর্ণ-মুখে চোখ বুজে দাঁড়িয়ে আছে। ওদিকে সামনে জীর্ণ স্যুট-পরা একটি নিষ্ঠুরদর্শন লোক। সুলতা বুঝতে পারলে, সেই হ্যারিস। আশেপাশে অনেক লোক। নারী-পুরুষ। তাদের চোখেও বিস্মিত দৃষ্টি।
বিস্ময় যার জন্য, সেটা সুলতার কাছে বোধ্য নয়। সে বুঝতে পারলে না তার অর্থ। কিন্তু তার রূপটা বিস্ময়কর বলেই তার মনে হল।
একটা কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী, সেই কুণ্ডলীর মধ্যে উপরের দিকে একটা মুখ। একটা মুখ নয়। পর পর তিনটে মুখ। একটার উপর আর একটা, তার উপর আর একটা। সব থেকে তলার মুখখানার ঘের সব থেকে বড়। তার মাথায় ঝাঁকড়া চুল। তার উপরে যেখানা, তার চুল বেশবিন্যাস করা। এ-দুখানা মুখের চুল এবং কপাল ছাড়া কিছু দেখা যাচ্ছে না। তার উপর যে মুখখানি, সে মুখটির সবটাই দেখা যাচ্ছে। সুন্দর সুপুরুষ, যেন অনেকটা সুরেশ্বরের মতো দেখতে। মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, পাকানো গোঁফ। কিন্তু সে-মুখ জীবন্ত মানুষের নয়, মরা মানুষের মুখ। মনে হয় নিষ্ঠুর যন্ত্রণার মধ্যে মারা গেছে। তার ছাপ রয়েছে মুখের মধ্যে।
ছবিখানার দিকে সে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।
সুরেশ্বর বললে, সুলতা, সেদিন গোয়ানপাড়ার জনতার সামনে যেন সেই আরব্য উপন্যাসের গল্পের বোতলে বন্দী দৈত্যটার বোতল থেকে বেরিয়ে পড়ার মত বেরিয়ে পড়ল রায়বংশের কবর-চাপা-দেওয়া ইতিহাসের এমনি একটা মূর্তি। ওই গোয়ান-বুড়ী হিলডা পুরনো কালের যাদুকরের মত উচ্চারণ করলে যাদুমন্ত্র। আর সঙ্গে সঙ্গে রায়বংশের সযত্নে তৈরী করা সমাধি ফাটিয়ে বের হল রায়বংশের পাপ অপরাধ, হয়তো বা ব্যাধি! ধর্ম সংসারে মানুষকে ঈশ্বর এবং স্বর্গ বৈকুণ্ঠ না দিক, তাকে পুণ্য দেয়, পবিত্রতা দেয়, জীবনে পরমানন্দ দেয়, শান্তি দেয়। সেই ধর্মের মধ্যে পাপ প্রবেশ করলে তখন আর রক্ষা থাকে না। মানুষের জীবনে বংশে এর নিগ্রহ থেকে মানুষের নিষ্কৃতি মেলে না। ঈশ্বর যদি থাকেন, তাঁরও সাধ্য নাই এ থেকে নিষ্কৃতি দিতে।
রায়বংশে সেই পাপ সঞ্চিত আছে।
সম্পদ-সঞ্চয়ের ইতিহাস বা তত্ত্ব সম্বন্ধে আধুনিক-কাল যাই ব্যাখ্যা করুক সুলতা, যে-কালে এই ব্যাখ্যার উদ্ভব হয়নি, সে-কালে সম্পদ সে-কালের ন্যায়-নীতির পথে অর্জন করে, মানুষের অনেক কল্যাণ করে গেছে। তাদের নাম আজও করে মানুষ। ইতিহাসের পাতায় তাদের নাম বেঁচে থাকবে। কিন্তু সম্পদ-সৌভাগ্য যারা অর্জন করতে পাপকে ইচ্ছে করে আশ্রয় করেছে, পাপ তাদের রক্তের মধ্যে আশ্রয় করেছে, পুরুষানুক্রমে চলে এসেছে। লোকের নিন্দার কথা ইতিহাসে বা লোকশ্রুতিতে বীভৎস কালো অক্ষরে তাদের নামের পাশে লেখা তো থাকেই, তার চেয়েও বেশী, বংশাবলীও সেই ধারাকে বয়ে নিয়ে চলে।
ওই প্রথম যে মুখখানা, সে রায়বংশের ধর্মসাধনার মধ্যে প্রবেশ করা পাপ। দ্বিতীয় মুখখানা সম্পদ-সৌভাগ্যের মধ্যে প্রবেশ করা পাপ। আর তার মধ্যে যে মুখখানা পুরো দেখতে পাচ্ছ, যার মধ্যে আমার চেহারার আদল রয়েছে, সে মুখ হল রায়বংশের শ্রেষ্ঠ রূপবান, লৌকিক বিচারে শ্রেষ্ঠ গুণবান, শ্রেষ্ঠ অভিজাত, শ্রেষ্ঠ প্রগতিশীল বংশধর যিনি তাঁর। মুখে তাঁর অসহায় ভাব দেখ, যন্ত্রণাকাতর অভিব্যক্তি দেখ। তিনিও পরিত্রাণ পাননি। আত্মা তাঁর আর্তনাদ করে।
সুরেশ্বরের কণ্ঠস্বর আবেগপ্রবণ হয়ে উঠেছিল। বোধহয় সেটা সে নিজেই বুঝতে পারলে। কারণ হঠাৎ সে স্তব্ধ হয়ে গেল। তারপর একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে—
হিলডা হ্যারিসের কথায় রাগে যেন একমুহূর্তে পাগল হয়ে গেল, তীক্ষ্ণকণ্ঠে চীৎকার করে উঠল-বাড়ী? ওই বাড়ীর ঘরের দাবী তুই করিস, খুনে শয়তানের বাচ্চা, খুনে শয়তান! তোর মা ওই ঘর থেকে দিয়ে গিয়েছে? কি তার এক্তিয়ার ছিল দেবার? তোর বাপ তোর মায়ের সঙ্গে—
কুৎসিত কথা সে সুলতা। যার অর্থ হল, হ্যারিসের মা তার বাপ ওই খাঁটি ইংরেজ প্রৌঢ় সার্জেন্টটির প্রেমে পড়ে ষড়যন্ত্র করে গোপনে মদের সঙ্গে কিছু খাইয়ে তার প্রথম স্বামীকে একরকম মেরে ফেলেছিল। বাড়ীটা ছিল কুইনির মায়ের বাপ রোজারিও পিদ্রুসের। হ্যারিসের মায়ের প্রথম স্বামীর। ও-বাড়ি রোজারিও পেয়েছিল—
হিলডা চীৎকার করে বলেছিল, রায় জিমিদারবাবু, রায়বাহাদুর উ বাড়ী দিয়েছিল তাকে। জরিমানা। হাঁ, জরিমানা। দলিলে লিখা আছে, উ বাড়ী রোজারিওর লেড়কা-লেড়কী পাবে, আর কোই পাবে না। ভায়লা—ভায়লেট পিদ্রুস। মেমলোকের মতুন সুরত ছিল তার। গোপাল পাল—
ঘড়িটা বাজতে শুরু করলে এই মুহূর্তে।
ঢং ঢং ঢং—
ছটা বেজে গেছে। সুরেশ্বর বলে চলল। সে-কাহিনী সুদীর্ঘ, তবু তার যতটা বলা যায়। সুলতা স্থিরদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল। গোপাল পাল তার ঠাকুরদাদা কাকা। ঠাকুরদাস পালের ছেলে।
গোপাল পাল!
হিলডা বলেছিল সুলতা, ‘গোপাল পাল’। তুমি বুঝতে পারছ তিনি কে? গোপাল পাল রায়বাহাদুরের বড়া বেটার ইয়ার ছিল। সেই নাকি ভায়লেটকে রায়বাবুর বড় ছেলের প্রলোভন দেখিয়ে তাকে এই গোয়ানপাড়া থেকে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়েছিল কলকাতা। তার ছেলে রোজা পিদ্রুস। গোপাল উকে ফেলে চলে গেল। রায়বাহাদুরবাবু দেখলে, কলকাতার বাড়ীর দরওয়াজা পর বোসে ভায়লা কাঁদছে। রায়বাহাদুর সব জানলে। দরওয়াজার ধাক্কা মারলে। ডর লাগলো রায়বাবুর বড়া বেটার। ডরসে বন্দুক নিয়ে খুন হতে গেল। আর গোপাল পাল ভাগলো। রায়বাহাদুর তখন জরিমানা দিলে। জরিমানা দিলে গোপাল উনার বড়া বেটার ইয়ার বলে। ভায়লার দাদা, আমার বাবা যে রায়সরকারে নালিশ করলে, বিচার করো হুজুর। গোপালের বাপ বললে, আমার লেড়কার দোষ কাঁহা? দোষ উ ছুকরীর। সো গেল কাহে? গাল দিলে। আজ ই ছোকরাকে সাদী করলে, কাল তাকে ছাড়লে, ফের সাদি করলে দুসরা ছোকরাকে। বাবা হামার খুন করলে গোপালের বাবাকে। রায়বাহাদুর জিমিদার, ধরমকে মানে, ধরমকে হিসাবসে বিচার। হামারা বাবার মামলামে বহুত খরচা করলে। তব ভি ফাঁসি হোয়ে গেল। রায়বাহাদুর ইসকে লিয়ে গুণাগারি দিলে। পিদ্রুসের বেটী এই হিলডাকে জমীন দিলে। এ সারা পাড়ার মণ্ডলান দিলে। রায়বাবুর দলিলে লিখা আছে কি,—এই বাড়ি ভায়লার লেড়কা রোজারিওকে দিলাম। ভায়লা সাদি করবে, উর লেড়কা না পাবে। রোজারিওর বেটা পাবে, বেটী পাবে—দুসরা কোই না পাবে। ওহি বাড়ির কামরা তোকে দিবে? তোর মা—উ দিবার কে?
হিলডার চীৎকারে অত্যন্ত কদর্য হয়ে উঠেছিল জায়গাটা। হ্যারিস তার দিকে ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল। তার নেশা বোধহয় ছুটে গিয়েছিল, কারণ এসব ইতিহাসের সে কিছুই জানত না। এবং না জানার জন্যে যত দুর্বোধ্য ঠেকছিল, ততই মনে হচ্ছিল, এর জবাব নেই, এ অকাট্য। কিন্তু আমি ভাবছিলাম, রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায়ের ডায়রির কথা। তার কিছুটা আমি বলেছি। গোয়ানপাড়ার মেয়ে ভায়োলেটকে দেবেশ্বর রায়ের ভাল লেগেছিল। কিন্তু কীর্তিহাটের সিংহ রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায়ের ভয়ে তিনি এখানে কিছু করতে পারেননি। তিনি কলকাতায় গেলে তাঁর সহচর গোপাল পাল তাকে এখান থেকে লুকিয়ে নিয়ে গিয়ে তুলেছিল কলকাতায়
গ্রামে গোয়ানদের মধ্যে তখন খুব হৈ-চৈ। তারা খুঁজছিল ভায়োলেটকে। ভায়োলেট গোয়ানদের প্রধান পিদ্রুসের সৎ-বোন। তাদের বাপ এক, মা পৃথক। তারা কেউ সন্দেহ করতে পারেনি যে, দেবেশ্বর রায়ের সহচর তাকে নিয়ে গেছে কলকাতায়। তারা ভেবেছিল, সে নিরুদ্দেশ হয়েছে তাদেরই মতন যারা তাদের কারুর সঙ্গে। যারা খানিকটা বন্য, খানিকটা উদ্দাম, তাদের মতো, তাদের কোন দুঃসাহসীর সঙ্গে। তখন ছিল। কাঁসাইয়ে নৌকা যেত-আসত। যেত সেই হিজলীর পাশ দিয়ে সাগরতীর্থ পর্যন্ত। ওপারের মুসলমানদের সঙ্গে যোগ ছিল তাদের। তীতুমীরের কথা পড়েছ। তীতুমীরের মতো দুঃসাহসী শক্তিমান মুসলমানরাও নৌকায় ডাকাতি করত। তারা আসত-যেত। কিন্তু কয়েকমাস পরে সত্য আবিষ্কার করেছিলেন নিজে রত্নেশ্বর রায়। তার ফল যা হয়েছিল বলেছি।
আমি ভাবছিলাম, তবে কি গোপাল পালই দোষী? আমি ভুল বুঝেছি তবে? মনে পড়েছিল বৃদ্ধ রঙলাল পালের কথা। তিনিও আমাকে তাই বলেছিলেন। ঠাকুরদাস পাল তাঁর পিসেমশাই হয়েছিলেন। বলেছিলেন—গোপালদাদা বড়বাবুর সঙ্গে ঘুরত। সেও মনে করত, সেও মস্ত বাবু। ভায়লাকে ভালবেসে নিয়ে পালিয়েছিল কলকাতা। রায়বাহাদুর কলকাতা গিয়ে হঠাৎ ভায়লাকে দেখতে পেয়েছিলেন। গোপালদাদা ভয়ে পালিয়েছিল। রায়বাহাদুরের কাছে খবর শুনে পিস খুন করেছিল ঠাকুরদাস পালকে।
সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়েছিল রায়বাহাদুরের ডায়রি। ঠাকুরদাস আমাকে অকস্মাৎ শাসিয়ে বললে—তুমিও জেনো, ছেলেকে শাসন করলে আমি সব ফাঁস করে দোব। আমি জানি, তোমার গুষ্ঠীর সব খবর আমি জানি। হ্যাঁ, আমি সব শুনেছি, আমি জানি। পুষ্যিপুত্তুর নেয়ার খবর আমি জানি।
রায়বাহাদুর চমকে উঠেছিলেন। তারপর ইশারা করেছিলেন পিদ্রুসকে। মনে মনে আমার, সেই সযত্নে ঢাকা-দেওয়া রায়বংশের অর্জিত মহাপাপের কথা ঠিক এমনিভাবেই যেন মাটি ফাটিয়ে এই ছবিটার মতো আমার সামনে ভেসে উঠেছিল।
বুঝতে আমার বিলম্ব হয়নি, এখানেও রায়বাহাদুর সুকৌশলে সব অপরাধ চাপিয়ে দিয়েছিলেন গোপালের উপর।
সুলতা! সম্পদ হল লক্ষ্মী। ভূমিতে আর মায়ে প্রভেদ নেই। দুইকেই আমরা ভাবি দেবতা। মানুষ সেই লক্ষ্মীকে ঘরে এনে লক্ষ্মীশ্বর নাম নেয়। ভূমি—জমিদারীর নামে কিনে ভূস্বামী হয়। সন্তান থেকে স্বামীত্ব দাবী করে। সে যে কতবড় অপরাধ, সে বোধহয় কেউ ভেবে দেখেনি কোনকালে। প্রজার রাজা সেজেই থাকেনি এদেশে জমিদারেরা। বোধহয় জান, রাজায় এবং প্রজায় এদেশে সম্বন্ধে বাপ-বেটা—এটা জমিদারের কথা। এ অপরাধের অবশ্যম্ভাবী ফল ভূস্বামীর বংশে-বংশে ঘটে এসেছে। এদেশে ওদেশে সব দেশেই ঘটেছে। এই অপরাধের সঙ্গে রায়বংশে অমার্জনীয় অপরাধ, ভীষণতম অভিশাপ অশেছিল, তাদের পূর্বপুরুষের ধর্মসাধনার মধ্যে।
ধর্মসাধনা করতে গিয়েছিলেন সন্ন্যাসী হয়ে। শক্তিসাধনা। বিমলাকান্তের বাপ শ্যামাকান্ত। সেই তান্ত্রিক সন্ন্যাসী—যাঁকে সোমেশ্বর পেয়েছিলেন কালীঘাটে। যিনি কীর্তিহাটে এসে যজ্ঞ করেছিলেন। কবচ দিয়েছিলেন। বলেছিলেন—পুত্রই হোক আর কন্যাই হোক, নাম দেবে ব অক্ষর দিয়ে।
তন্ত্র সত্য হোক বা না হোক, বিশ্বাস কর বা না কর, সোমেশ্বরের এক কন্যা, এক পুত্র এরপর বেঁচেছিল, এটা বাস্তব সত্য।
এই ছবির এই যে ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মধ্যে পর পর চাপানো তিনটে মুখ, এর প্রথমটা সেই শ্যামাকাণ্ডের। দ্বিতীয়টা সোমেশ্বরের। তৃতীয়টা দেবেশ্বরের।
বংশানুক্রমের ধারা বিচিত্র গতিপথে বেয়ে এসেছে। বংশধারার স্রোতের সঙ্গে মহাপ্রকৃতির, মহাশক্তির অভিশাপ
সুলতা অসহিষ্ণু প্রশ্ন করলে—তুমি এসব কি বলছ সুরেশ্বর? সুলতার সন্দেহ হল, সুরেশ্বরের মাথার গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। রাত্রে যখন সে প্রথম তাকে বলতে আরম্ভ করে তাদের বংশের কাহিনী, তখন জনশূন্য ঘরটায় শুধুমাত্র তাকে সামনে রেখে সে সম্বোধন করেছিল, লেডিজ এন্ড জেন্টলমেন!
তারপরই ভ্রম বুঝতে পেরে বলেছিল-আমার মনে হচ্ছে সুলতা, এই ঘরে আজ অনেক লোক এসে বসেছেন। ওই ছবির মানুষগুলির আত্মাদের উপস্থিতি আমি বুঝতে পারছি।
সুরেশ্বর বললে—তুমি বুঝতে পারছ না, না?
—না। অর্থ থাকলে তো বুঝব। এ কথার কি কোন অর্থ হয়?
—অর্থ আছে, কিন্তু তোমাদের না বোঝারই কথা। কিন্তু বল তো, রাশিয়ার বিচিত্র মানুষ রাসপুটিনের কথার অর্থ আছে? বিশ্বাস কর?
সুলতা বললে—তার আসল সত্য কতটা জানি না, তবে মানুষটা ইতিহাসের মানুষ। সে এক ধরনের কিছু একটা জানত। যাতে জারের ছেলেকে সে বাঁচিয়েছিল। তার কলঙ্কও অনেক।
—ভাল সুলতা। এদেশে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে অন্তত সেই হিসেবে অবশ্যই মান। আমি জানি, এ-যুগে অনেকে তাঁকে মনে মনে অস্বীকার করতে চেষ্টা করে। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের জন্যে তা পারে না। তুমি তাঁকে মানো বা নামানো, তাঁর কথা জান নিশ্চয়।
সুলতা স্থিরদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল।
সুরেশ্বর বললে—বল!
সুলতা বললে-আমি ব্রাহ্ম বলে বলছ এ কথা?
—না। ব্রহ্মানন্দ কেশব সেন রামকৃষ্ণকে অসাধারণ শ্রদ্ধাভক্তি করতেন। ব্রাহ্ম বলে নিশ্চয় বলিনি। বলছি, তুমি রাজনীতিতে, শিক্ষায় খাঁটি একালের মানুষ। তার উপর নিজে রাজনৈতিক পার্টির সভ্য।
সুলতা হাসলে, বললে—একালের উপর তোমার রাগটা সেকালের লোকের মত। যাক, যা বলছিলে তাই বল। সকাল হয়ে এসেছে। পালা শেষ কর
সুরেশ্বর বললে, পালার এখনও অনেক বাকী সুলতা। তোমার সময় নেই বলে আমার তো শেষ হবে না। আজ সন্ধ্যায় আসতে বলব। যদি না আস, তবে নাইবা থাকলে তুমি, আমি পথের লোক ডেকে এনে শোনাব। তোমাকে লিখেছিলাম, তোমার কাছে আমার ফিরে যাওয়া অসম্ভব। কেন অসম্ভব সে কথাটা তোমাকে বলেছি। তোমার আমার মাঝখানে আমার পূর্বপুরুষের খাঁড়াঘাতে তোমার পূর্বপুরুষের রক্তস্রোত বইছে। সেইটে যখন জানলাম, তখন ও-লেখা ছাড়া আমার উপায় কি ছিল। তবে তোমার প্রপিতামহ গোপাল ঘোষ রায়বাহাদুরের কাছে খেসারতের দাম নিয়েছিলেন হাত পেতে, সেদলিল আছে। আর ভায়লেটকে নিয়ে পরবর্তীকালে তাঁর অপবাদকে সত্য করে তুলেছিলেন। যাক, সেসব কথা শুনলে বুঝতে পারবে না। এখন যে অপরাধের কথাটা বলেছিলাম, তাই বলি।
সেদিন গোয়ানপাড়ার কোলাহলের মধ্যে এই ছবিটা যখন আমার মনের চোখে ভেসে উঠেছিল, সেদিন সেই মুহূর্তটা আমার কাছে জীবনের সব থেকে ভয়ঙ্কর মুহূর্ত। যতবার হিলডা বলেছে গোপাল ঘোষের নাম, ততবার মনে হয়েছে, রায়বংশের এঁরা মাথা হেঁট করে অপরাধীর মত দাঁড়িয়ে আছেন। চোখ থেকে তাঁদের জল পড়ছে। তাঁরা সহস্র যন্ত্রণা ভোগ করছেন। হিলডাকে চুপ করতে বলতেও আমার শক্তি ছিল না। হঠাৎ কুইনি চীৎকার করে উঠেছিল—তুমি চুপ কর। তুমি চুপ কর দিদা।
হিলডা তবুও থামেনি।
তীক্ষ্ণকণ্ঠে কুইনি চীৎকার করে উঠেছিল এবার—দি—দা!
আশ্চর্য সে চীৎকার। সেরকম চীৎকার করে বারণ করলে বোধহয় দুনিয়ার কেউ তা লঙ্ঘন করতে পারে না। এবং হিলডাও পারেনি। চুপ করে গিয়েছিল। গোয়ানদের গুঞ্জন থেমে গিয়েছিল। সব স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল একমুহূর্তে। আমি বুঝতে পেরেছিলাম কুইনির মন। তার পক্ষে এ কথাগুলি শোনা আমারই মত অসহ্য হয়ে উঠেছে। হয়তো বা আমার চেয়েও অসহ্য তার পক্ষে। পিতৃপুরুষের মধ্যে সব সমাজেই বোধহয় পুরুষের কলঙ্ক থেকে নারীর কলঙ্কের জ্বালা বেশী, তার ওজন বেশী। ভায়লেট তার মাতামহের মা। সে তার সহ্য-সীমার শেষপ্রান্তে এসে এই চীৎকার করে উঠেছিল। সে গোয়ানদের মধ্যে বাস করলেও এদের থেকে পৃথক। বলতে গেলে অনেক দূরে বাস করে মানসিক জগতে। সব স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল।
সেই স্তব্ধতার মধ্যে সে বলেছিল—uncle Harris—I refuse to go with you. I refuse to give you the room you claim as yours. You please go back and do whatever you like. Roy babu has got no right to interfere in my affairs.
বলেই সে চলে গিয়েছিল।
আমিও চলে এসেছিলাম ফিরে। সারা পথটা মাথা হেঁট করে ভাবতে ভাবতে এসেছিলাম। বার বার মনে ঘুরছিল রায়বংশের এই অপরাধের কথা। ছবিটা মনের মধ্যে যেন রঙে রঙে ফুটে উঠছিল। কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মধ্যে এই তিনটি মুখ একের পর এক থাকে থাকে ফুটে উঠেছে।
শ্যামাকান্ত শক্তিসাধনার জন্য গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়েছিলেন। তিনি পরমাশক্তিকে মাতৃভাবে পেতে চাননি, চেয়েছিলেন পুরুষে যেমন করে নারীকে পেতে চায় তেমনিভাবে। তার ফল হল ভীষণ। অভিশপ্ত হলেন নিজের জীবনে। জান্তবজীবনের প্রকৃতি পেলেন।
সোমেশ্বর রায়-সৌভাগ্যশিলার লোভে এবং তাঁর এই পথে সাধনসঙ্গিনী এক ব্রাত্য-নারীর লোভে—তাঁকে মেরে ফেলতে চেয়েছিলেন। লোকে জানত তিনি মরেছেন। কিন্তু শ্যামাকান্ত মরেননি তাঁর দুর্ভাগ্যক্রমে। বেঁচেছিলেন। তারপর সন্ন্যাসী হয়েও আবার বিবাহ করেছিলেন সস্ত্রীক সাধনা করবার উদ্দেশ্যে।
রামকৃষ্ণদেব সারদাদেবীকে দেবতা হিসেবে অর্চনা করেছিলেন শুনেছ কিনা জানি না। তিনি তাঁর মধ্যেও মাতৃরূপকে দেখেছিলেন। শ্যামাকান্তের উল্টো হল। তাঁর পত্নীর গর্ভে সন্তান জন্মাল। কন্যা।
উন্মাদ পাগল হলেন শ্যামাকান্ত। ছুটে পালালেন। কিন্তু তাঁর সাধনা তাঁকে ছাড়বে কেন? তিনি এক বিধর্মী নারীর মোহে বাঁধা পড়লেন। জাত হারালেন।
রায়বংশের তপস্বিনী বউ ভবানী দেবীর বাপের নাম তাই তাঁর পালক পিতা গোপন রেখেছিলেন।
ভবানী দেবী বিমলাকান্তের বৈমাত্রেয় ভগ্নী। শ্যামাকান্তের সাধনার মধ্যে যেটুকু পুণ্য ছিল, তাই নিয়ে তিনি জন্মেছিলেন।
কমলাকান্ত-রত্নেশ্বর রায়ের সঙ্গে বিমলাকান্তের চেহারায় সে সাদৃশ্য ছিল, তা এসেছিল তাঁর মাতামহ থেকে।
রায়বংশে ওই লালসা- সম্পদের সাহায্যে-এমনভাবে আগুন হয়ে জ্বলছে যে সমস্ত পুড়িয়ে ছাই করে দিতে চেয়েছে। যত লালসা, যত পতন, তত জ্বালা, তত উন্মত্ততা।
অন্তত এইটেই বিশ্বাস হয়েছে আমার। তাঁদের কাগজপত্রে, কারুর ডায়রীতে, কারুর চিঠিপত্রে, কারুর খরচের খাতায় এর পরিচয় তাঁরা রেখে গেছেন। আমার মধ্যেও সে তাড়না আমি অনুভব করেছি।
তাঁদের জীবনের ঘটনায় রচনায় তার পরিচয় পদে পদে অক্ষরে অক্ষরে। তবে বিচিত্রভাবে বংশ-পুণ্য তার প্রায়শ্চিত্তও করে যাচ্ছে। সে কাহিনী না শুনলে। ঘাড় নাড়লে সে। যার অর্থ তা না শুনলে বুঝতে পারবে না। কিছুক্ষণ পর বললে—আর তাই বোধহয় ইতিহাসের ধারা।
কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল দুজনে। ঘড়িতে আধঘণ্টা বাজল। ঢং শব্দে।
তারপর সুরেশ্বর ডাকলে—রঘু।
—যাই!
রঘু এসে দাঁড়াল।
—একটু চা কর। রঘু চলে গেল।
সুলতা বললে, না। আমি যাব এবার সুরেশ্বর।
—যাবে? চা খেয়ে যাবে না?
—না। তবে এ নিয়ে তুমি এমন করে নিজেকে আধ-পাগল করে তুলেছ কেন, তা আমি বুঝতে পারি না। ইতিহাসের ধারায় এক-একটা ধারা এসেছে, আবার ইতিহাসই তাকে মুছে দিয়েছে।
সুরেশ্বর তার মাথার রুক্ষ চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে অবিন্যস্ত লম্বা চুলগুলোকে বিন্যস্ত করে নিয়ে বললে—দেখ, ইতিহাস পুরনো ধারাকে বদলে নূতন ধারা আনে কিনা জানি না। তবে নতুন একটা চেহারা নেয়। কিন্তু মানুষের মধ্যে আর একটা ধারা আছে। সেটা তার মনের ধারা চিন্তার ধারা থেকেও আরও গভীরে বইছে। সে এই চেহারা বদলেই তুষ্ট হয় না। সে প্রায়শ্চিত্ত করতে চায়। পরিণাম আর পরিণতিতেই তার বিশ্রাম নেই; পূর্ণতার জন্যে সে জন্মজন্মান্তর ঘুরছে—এইটেই তার বিশ্বাস। অন্য দেশ দেখেছি। সামান্যই দেখেছি। কিন্তু এদেশে সেই বিশ্বাস আজও সমান দৃঢ়, তা আমি অনুভব করছি বলেই এমন না হয়ে আমার উপায় ছিল না। উঃ কি সংগ্রাম সুলতা। গোটা রায়বংশের সাতপুরুষের সংগ্রাম আমার এই তেতাল্লিশ বছরের জীবনে ঘটে গেল। আমি—
কথায় বাধা দিয়ে রঘু এসে ঢুকল। রঘু অবশ্য বাধা নয়। বাধা ছিল তার পিছনে। তার পিছনে একটি মেয়ে
আশ্চর্য সুন্দরী মেয়ে। পুর্ণ যুবতী। বলতে হয় অপরূপা। বিধবা মেয়ে। সুরেশ্বর চমকে উঠল তাকে দেখে। সুলতাও উঠল। মনে হল মুখখানা যেন চেনা। পর মুহূর্তেই তার এই ‘চেনা’ মনে হওয়ার কারণটা মনে পড়ল এবং আপনাআপনি তার দৃষ্টি গিয়ে নিবন্ধ হল সামনের দেওয়ালের দিকে, যেখানে ভবানী দেবীর পূর্ণাবয়ব অয়েলপেন্টিংখানা ঝুলছিল সেইখানে। আশ্চর্য সাদৃশ্য তো। শুধু ভবানী দেবী অলঙ্কারে, বেনারসী শাড়ীতে, সিঁথির সিঁদুরে স্বামীসৌভাগ্যবতী, রাজরানী, আর এ মেয়ে নরুণপেড়ে সাদাজমি কাপড়-পরা, নিরাভরণা, খালিহাত, যেন সর্বরিক্তা। তাছাড়া ভবানী দেবী উজ্জ্বল শ্যামাঙ্গী। এ মেয়ে গৌরাঙ্গী। রূপের মধ্যে একটি মহিমা আছে।
সুরেশ্বর বিষণ্নতার মধ্যেই বিস্ময়ে একটু চঞ্চল হয়ে উঠল। বললে—অৰ্চনা?
হেসে অর্চনা বললে-হ্যাঁ গো আমি। ভূতটুত নই। জ্যান্ত অৰ্চনা।
—হঠাৎ তুই কোত্থেকে এলি? তীর্থ থেকে সরাসরি?
—না। কীর্তিহাট হয়ে আসছি।
—কীর্তিহাট হয়ে? সেখানে কবে এসেছিস? এক সপ্তাহ আগেও তো আমি গেছি সেখানে।
—ওখানে এসেছি পরশু সকালে।
বলে এবার সে প্রণাম করলে সুরেশ্বরকে। হেসে সুরেশ্বর বললে—প্রণাম! তাও একটা?
—তাহলে গোটাকতক মাথা ঠুকব নাকি পায়ে?
—উঁহু।
—তবে?
—তাহলে দে, মাথায় হাত বুলিয়ে দে, পুণ্যি হোক, পাপটাপ খণ্ডে যাক। মাথাটা নোয়ালে সুরেশ্বর।
অর্চনা বললে-তা হবে না মনে কর নাকি? নিশ্চয় হবে। বলে সে সত্যিই তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলে।
সুরেশ্বর এবার হাত পেতে বললে-এবার প্রসাদ?
—সে আছে। সব আছে। কাশীর পেঁড়া আছে, পেয়ারা আছে। বৃন্দাবনের চিনির মুড়কি আছে, এলাচদানা আছে। মায় সাবিত্রীর সিঁদুর আছে। আর জয়পুর থেকে অনেক জিনিস কিনে এনেছি। কিন্তু তার আগে, তুমি কি মানুষ বল তো, এঁর সঙ্গে মানে সুলতাদির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়াটা তো উচিত।
—ওই তো, আলাপের বাকি রইল কি? আলাপ তো হয়ে গেছে। নাম তো দেখছি শুনেই ফেলেছিস।
—হ্যাঁ, রঘু বললে, সারারাত্রি ছবি দেখিয়ে রায়বংশের কাহিনী বলেছ। আমার কথাও তাহলে বলেছ তো।
—বলেছি বৈকি। রায়বাড়ীতে আমার কথা তুই আর মেজদি আর অতুলেশ্বরকে বাদ দিয়ে কি বলা চলে? কিন্তু শেষ হয়নি। নে, মুখ-হাত ধুয়ে নে—
—তার আগে তুমি এক্ষুনি নীচে যাও।
—কেন?
কুটুম্ব-জ্ঞাতির দল, বিষয়ের শরিকের দল নীচে বসে আছে।
—মানে?
—মানে কল্যাণদা হেড পাণ্ডা, তার সঙ্গে বিমলেশ্বরকাকা, আমার দাদা অমরেশ্বর, ব্রজেশ্বরদার ভাই রাজেশ্বর মায় প্রণবেশ্বরদা—সব দল বেঁধে এসেছে। ব্রজেশ্বরদা-ও এসেছে। আমি পরশু এসেছি। এসেই দেখি, বিকেলবেলা কাগজ নিয়ে নাটমন্দিরে বসে জমিদারী উচ্ছেদের বিবরণ পড়া হচ্ছে। কাল সব পরামর্শ করে আমার কাছে এসে বললে, তোকে আমাদের সঙ্গে যেতে হবে। আমরা সুরেশ্বরের কাছে যাব। জমিদারী উচ্ছেদ হচ্ছে, গোটা বংশটাকে পথে দাঁড়াতে হবে, দেবসেবা বন্ধ হবে। এর প্রতিকার এখন থেকে না করলে চলবে না। তাই আগমন। এসে সব নীচের হলঘরে বসেছে, আমাকে দূত করে পাঠিয়ে দিলে, খবর দে।
সুরেশ্বর হাসলে। সুলতার দিকে তাকিয়ে বললে—সুলতা, রাত্রি শেষ হয়েছে, সূর্য বোধহয় উঠছে; জমিদারী উচ্ছেদ বিল পাস হয়েছে, জমিদারী এখনও যায়নি, তাতে সময় লাগবে। ইতিমধ্যে মিছিল এসে পৌঁচেছে। আমাদের দাবী মানতে হবে। তোমার পলিটিক্সে এবং ইতিহাস-অর্থনীতির পণ্ডিত হিসেবে এটা কাজে লাগবে। এখনকার মত অ্যাডজোনৰ্ড। আজ
সন্ধ্যেতে তোমাকে আসতে বলব।
সুলতা বললে-তুমি যাও। আমিও বরং যাই।
—একটু বস। আমি লছমনকে বলে দিই একটা ট্যাক্সি নিয়ে আসুক। একটুক্ষণ অর্চনার সঙ্গে গল্প কর।
সে নীচে নেমে গেল।
সুলতা অর্চনাকে বললে—আপনি নীচে রঘুর কাছে আমার নাম শুনে কি করে চিনলেন আমাকে?
অর্চনা বললে-সুরোদা যখন সেটেলমেন্ট নিয়ে কীর্তিহাটে গেল, তখন সুলতার নামে চিঠি যেত, আবার সুলতার চিঠি আসত। ওই তো বাউণ্ডুলে মানুষ, চিঠি পড়ে থাকত। আমরা তো তখন আইবুড়ো, তখন কৌতূহল কত, পড়েছি চিঠি। মেজদিও আবার চিঠি শুনত। তারপর হঠাৎ কি হল, আপনার চিঠি বন্ধ হল ও-ও বন্ধ করলে।
চুপ করে রইল সুলতা।
অৰ্চনা বললে—তখন সুরোদা আধ-পাগল। সত্যি বলব আপনাকে, ভয় লাগত মধ্যে মধ্যে। যা খেয়াল হত তাই করত। একদিন শুনলাম, শরিকদের তিন হাজার টাকা দিয়ে গোয়ানপাড়ার গোয়ানদের বাড়ী-ঘর, গোটা পাড়াটা লাখরাজ করে দিয়েছে। সেইদিনই ছোটকা মানে অতুলেশ্বরকাকা অ্যারেস্ট হলেন, বাড়ী সার্চ হল, মেজদি আমাকে বাঁচাতে গিয়ে অ্যারেস্ট হলেন, জেল হয়ে গেল। এর পরই আমার বিয়ে হয়ে গেল। বাবা বিয়ে ঠিক করেছিলেন একজন পুলিশ দারোগার সঙ্গে। আমার মাথায় বাজ ভেঙে পড়ল। ভাবলাম বিষ খাব। জানেন, আমি অতুলকাকার সঙ্গে ওই সব কাজে জড়িয়ে পড়েছিলাম। বাঁচালে আমাকে সুরোদা। বাবার পায়ে-হাতে ধরে অনেক কষ্টে রাজী করে নিজে আট হাজার টাকা খরচ করে আমার বিয়ে দিলে ডাক্তার পাত্র দেখে। তখন ও দুর্দান্ত মদ খাচ্ছে। আমি আপনাকে চিঠি লিখব ভেবেছিলাম কিন্তু সুরোদা জানতে পেরে বলেছিল—খবরদার অর্চি, ও-কাজ করিসনে।
সুলতা অস্বস্তি বোধ করলে এবার, তার নিজের কথা এর মধ্যে নতুন করে জড়িয়ে ফেলাটা ভাল লাগল না তার। আবার কেন? সুরেশ্বর সম্পর্কে তার আর কোন আকর্ষণ নেই। তার এই নতুন জীবনে সে যে আনন্দ পেয়েছে, তাতে ঘর-সংসারের কামনা অত্যন্ত তুচ্ছ, ছোট হয়ে গেছে। তাছাড়া এই বয়সে, বয়স তো তার প্রায় চল্লিশের কাছে। আটত্রিশ পার হতে চলেছে, এখন বিয়ের কনে সাজবার কথা মনে হলে হাসি পায়। অর্চনা কথাটা ওই পর্যন্ত বলে হঠাৎ চুপ করে গেছে; সম্ভবতঃ এমন কোন কথা তার মনে পড়েছে, যা ওকে নিজের মধ্যে নিজেকে মগ্ন করে দিয়েছে, স্মৃতির মধ্যে বেদনার স্বাদ নতুন করে জেগে উঠেছে, হয়তো এখুনি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলবে। হয়তো ওর নিজের বিয়ের কথা—যার সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ছে বৈধব্যের কথা। অতি অল্পদিনের মধ্যেই যে অর্চনা বিধবা হয়েছে, তা ওকে দেখেই বোঝা যায়। যার ধাক্কায় সেদিন কুমারী বয়সে যে অর্চনা ওর ছোটকাকার সঙ্গে আগুন নিয়ে খেলতে নেমেছিল, সে নিজের চোখের জলে ভিজে অঙ্গার হয়ে গেছে। সে আজ তার এই জীবন, এই মন বুঝতেই পারছে না। তাকে প্রীতি-আদরের স্নেহসিঞ্চনে ভিজিয়ে নরম করে টানতে চাচ্ছে, তার সমাদরের সুরোদার দিকে। একটু হাসি ফুটে উঠল তার মুখে।
অর্চনা ঠিক এই মুহূর্তে তার দিকে তাকাল এবং জিজ্ঞাসা করলে-হাসছেন কেন সুলতাদি?
সুলতা চট করে উত্তরে বলবার কথা খুঁজে পেলে, কথাটা অনেকক্ষণ থেকেই তার মনে উঠে দাঁড়িয়ে রয়েছে অপেক্ষা করে। যখন নিজেই সে প্রশ্ন করেছিল—রঘুর কাছে আমার নাম শুনে কি করে চিনলেন আমাকে? সেই তখন থেকে। সে বললে—হাসছি ভাই, আপনাকে কিন্তু আমি আপনার নাম শুনবার আগেই দেখে চিনেছি, আপনি অর্চনা। রায়বাড়ীর মতো বাড়ীর মধ্যে স্বদেশী-করা মেয়ে! ওই ওঁর ছবির সঙ্গে আপনার মিল দেখে।
অর্চনা তার মুখের দিকে তাকিয়ে বিষণ্ণ হেসে ভবানী দেবীর অয়েলপেন্টিংটার দিকে তাকিয়ে হাতজোড় করে প্রণাম করে বললে—হ্যাঁ, ওঁর সঙ্গে আমার চেহারার মিল আছে। কিন্তু উনি জন্মেছিলেন দেবতার অংশে। নিজের সাধনভ্রষ্ট বাপকে উদ্ধার করেছিলেন। ওঁরই পুণ্যে রায়বংশে অতুলকা জন্মেছে, সুরোদা এসেছে। ওঁর সঙ্গে আমার চেহারার মিল, এক বংশ বলে। আমার স্বামী ডাক্তার ছিলেন, বলেছিলেন আমাকে। এমন হয়। ওঁর পুণ্য আমি কোথায় পাব? ওঁরা বলে—আমি হাসি। কি বলব? অতুলকা জেল থেকে খালাস হয়ে বিয়াল্লিশের সাইক্লোনের পর নিউমোনিয়া হয়ে যখন শয্যাগত তখন আমাকে ওই কথা বলেছিল—অর্চি, এ বংশের পুণ্যটুকু তোকে ধরতে হবে বলেই তো এই দুঃখ, তুই বিধবা হয়েছিস। মা চলে গেছে বৃন্দাবন, রায়বাড়ীর দেবসেবার ভার তোর ওপর। সুরো—
কথা সে শেষ করতে পারলে না; নিচেরতলা থেকে একটা উচ্চ উত্তপ্ত কণ্ঠস্বর ভেসে এল—তুমি কি আমাদের ভিখিরী মনে কর নাকি? কি ভাব তুমি?
চমকে উঠল অৰ্চনা। কান পেতে রইল। চোখ তার সুলতার দিকে নয়, চোখ তার ঘরের ছাদের দিকে।
আবার সেই গলার আওয়াজ উঠল—নিশ্চয় তাই ভাবছ তুমি! হাজারবার বলব—তাই ভাবছ তুমি!
অর্চনা এবার উঠে পড়ল! বললে—একটু বসুন ভাই, আমি নিচে গিয়ে দেখি। কি বলব—পচে গেছে, বুঝলেন, সব পচে গেছে। ঝগড়া শুরু করে দিয়েছে। আমি দেখি। সুরোদা যদি এর উপর রেগে যায় তো অনর্থ হবে। সুরোদা ওইটে আর ছাড়তে পারলে না। মাঝে মাঝে এমন ক্ষেপে যায়—
অর্চনা পা বাড়ালে, সুলতা উঠে দাঁড়িয়ে বললে—চলুন আমিও যাই। ট্যাক্সি এসে থাকবে এতক্ষণ। না এলে একটু দাঁড়াব।
—না। বসুন। ট্যাক্সি এলেই রঘু বা লছমন এসে ডাকবে। ওখানে নিচে দাঁড়িয়ে রায়বংশের এদের যে চেহারা দেখে যাবেন, তাতে সুরোদা লজ্জা পাবে, আমিও পাব। একটু বসুন।
সুলতা অগত্যাই বসল। কথাটা সত্যি বলেছে অর্চনা। রায়বংশের জ্ঞাতিকলহের মধ্যে গিয়ে পড়ে সেও বিব্রত হবে, সুরেশ্বরও হবে, হয়তো বা আরও দু-একজন হবে, কিন্তু দু-একজন বিব্রত হওয়ার সীমানা পার-হওয়া মানুষ, তারা গ্রাহ্য করবে না। ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ নিশ্চয়, কারণ ওরা দল বেঁধে এসেছে। অৰ্চনাকে নিয়ে এসেছে, ওদের স্বার্থের ব্যাপার।
একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস আপনি ঝরে পড়ল তার বুক থেকে। যতক্ষণ প্রাচুর্যের মধ্যে আছে মানুষ, ততক্ষণই সে মানুষ। প্রাচুর্যের মধ্যে মানুষ অন্যায়-অবিচার মনুষ্যত্বের ব্যভিচার অনেক করে, কিন্তু তার মধ্যেও প্রতিষ্ঠা, গৌরব, আত্মতৃপ্তির জন্য মনুষ্যত্বের দীপ্তিকে প্রশ্রয় দেয়, লক্ষ্মীর ঘরের ঘিয়ের প্রদীপের মত জ্বালিয়ে রাখে, কিন্তু দারিদ্র্যের মধ্যে যখন নিচে নামে, তখন আর মনুষ্যত্বের একবিন্দু অবশিষ্ট থাকে না। লক্ষ্মীর ঘরের ঘিয়ের প্রদীপ নিভলেই মশাল জ্বালো, তাতেও অন্ধকার ঘুচবে না, মশালের কলিতে ধোঁয়ায় দম বন্ধ করে অন্ধকারকে ভয়ঙ্কর করে তুলবে।
আজও সুরেশ্বরের মহত্ত্ব, সুরেশ্বরের এই খেয়ালীপনার ঝকমকানি সব ভাল লাগছে এবং বাস্তবে সম্ভব হয়েছে, ওই লক্ষ্মীর ঘরের ঘিয়ের পঞ্চপ্রদীপে পাঁচ-পাঁচটা পলতের মুখে শিখা উজ্জ্বল হয়ে জ্বলছে বলে। সেকাল হলে সুরেশ্বর বীরেশ্বর রায় হত, না হয় রত্নেশ্বর রায় রায়বাহাদুর হত। সে তার ঠাকুরদার ঠাকুরদাকে—
আবার একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে সে। সুলতা উঠে গিয়ে দাঁড়াল, বীরেশ্বর রায় যে ছবিটার মধ্যে তাই তান্ত্রিক পাগলের গলা টিপে ধরেছেন। পাশে পায়ে ধরেছে সোফিয়া বাঈজী। তান্ত্রিক যন্ত্রণাকাতর মুখে হাঁ করে আছে।
সুরেশ্বর বললে—আঁ-আঁ। একটা আনুনাসিক জান্তব চিৎকার করছে।
কিছুক্ষণ ছবিটা দেখে, পাশের ছবির দিকে তাকালে। প্রকাণ্ড বড় ছবি একখানা। ঠিক মাঝখানে টাঙানো। একটা দরবারের ছবি।
ইংরেজ আমলের দরবার। পুরনো ইংরেজ আমল। সাহেবদের পোশাকে বোঝা যাচ্ছে। খুব জাঁকজমক করে সাজানো, ক’জন সাহেব উঁচু ডায়াসে বসে আছে, একজন একখানা কাগজ খুলে তা থেকে কিছু পড়ছে। সামনে দেশী লোকেরা বসে আছে। সামনের এঁরা রাজা জমিদার। চোগাচাপকান, পাগড়ি, শামলা, সোনার মোটা গার্ডচেন পরে বসে আছেন। পিছনে অনেক লোক। এদেশের কালো চামড়া বিস্ফারিত ভীত-দৃষ্টি ঘোলাটে চোখ। সুরেশ্বর শিল্পী হিসেবে প্রশংসার পাত্র, এ স্বীকার সে করবেই। এক্সপ্রেসন তার ভাল।
ফ্রেমের উপর ছবির নাম-লেখা কাগজটার উপর ঝুঁকে সে লেখাটা পড়তে চেষ্টা করলে। শতাব্দী শেষ। ১৮৫৮ সাল ‘কুইনস প্রক্লামেশন’- মেদিনীপুর দরবার। আবার সে ছবিটার দিকে তাকালে। এই যে বীরেশ্বর রায়ও বসে আছেন। প্রথম সারিতে বাঁ দিকে, সেভেন্থ চেয়ারে বসে আছেন।
সে উঠে দাঁড়াল। নিচের গোলমাল যেন বেড়ে উঠছে। অস্বস্তিবোধ করতে লাগল সে। এর মধ্যে বন্দীর মত দাঁড়িয়ে আছে সে। ক্রমশ অসহনীয় হয়ে উঠেছে। এখনও ট্যাক্সি এল না। তাহলে সুরেশ্বর ভুলেই গেছে ট্যাক্সির কথা বলতে। হ্যাঁ, তাই হবে। নিশ্চয় তাই। কিন্তু সে আর এখানে এইভাবে মুখ লুকিয়ে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে। না, সে আর থাকবে না।
এবার সে হনহন করে চলতে লাগল।
হঠাৎ প্রচণ্ড চিৎকারে কেউ ফেটে পড়ল-একদিন এর জবাবদিহি করতে হবে তোমাকে। কড়ায় গণ্ডায় বুঝে নেব! বুঝলে!
—কমলেশ্বর! কমলেশ্বর! থাম থাম!
—কেন থামব! চিৎকার করে বলব।
থমকে দাঁড়িয়ে গেল সুলতা। ঠিক এই মুহূর্তে নিচে নামতে তার পা উঠছে না। সিঁড়িটা যেখানে নেমেছে, নিচের বারান্দায়, তার কোলেই বড় ড্রয়িংরুমটা; একেবারে সামনে গিয়ে পড়তে হবে।
—কমলেশ্বর, কমলেশ্বর, তোমার পায়ে ধরছি আমি।
—তাতে আমার বয়েই গেল! দেবোত্তর! দুটো পাথরের পুতুল, সে খায় না, পরে না, তার সেবা! ও আমি মানি না! মানব না!
এবার বিচিত্র হাসি ফুটে উঠল সুলতার মুখে। ওই কথাটায় মুহ্যমানতা তার কেটে গেল। সামনের দেওয়ালের একটা ছবি তার চোখে পড়ল।
অন্ধকারের মধ্যে একটা আলো জ্বলছে। তারই আলোয় দেখা যাচ্ছে চারজন মানুষকে। পরিপূর্ণ আলো পড়েছে একজন শয্যাশায়ী লোকের মুখে। কে? মুখে দাড়ি-গোঁফ, মাথায় চুল। এ কি পাগল নয়? হ্যাঁ, পাগলই। কিন্তু এ পাগলের মুখের চামড়া কোঁকড়ানো নয়, মুখখানা কালো নয়। মসৃণ কপাল, রঙটা গৌরবর্ণ, সুপুরুষ মানুষ, চোখ থেকে জল পড়ছে, মুখ প্ৰসন্ন। পাশে আবছা হলেও চেনা যাচ্ছে বীরেশ্বর রায়কে, এপাশে ইনি ভবানী দেবী। আরও একজন। পায়ের তলায় বসে আছে। পিছনটা দেখা যাচ্ছে। ফ্রেমে লেখা, শাপমুক্তি। সংগ্রাম শেষ!
হঠাৎ সুলতার কানে এল—
—বেশ করি, আমি খুব করি। আমি যা করি তাতে আমার জাত যায়, না? আর ও, ওই সুরেশ্বর, ও যে ক্রীশ্চান, গোয়ান মেয়ে বিয়ে করেছিল, একটা লম্পট। খুব বেঁচেছে, মেয়েটা ওকে রেহাই দিয়েছে। ও দেবোত্তরের কে? দেবোত্তর ফলাচ্ছে!
চমকে উঠল সুলতা! সুরেশ্বর—ক্রীশ্চান গোয়ান মেয়ে—
—আজ আবার ওই তো একটা মেয়েকে নিয়ে সারা রাত-সঙ্গে সঙ্গে কোলাহল উঠল।
—সুরেশ্বর সুরেশ্বর-মরে যাবে, সুরেশ্বর। রাজাভাই! রাজা!
এবার অর্চনার কণ্ঠস্বর শোনা গেল, সুরোদা, সুরেশ্বরদা—
সুলতা আর থাকতে পারলে না, আর সহ্য হল না তার। সে দ্রুতপদেই দক্ষিণের বারান্দাটা অতিক্রম করে নিচে নেমে এল। চলেই সে যেত। কিন্তু ঘরের ঝগড়াটা তখন বাইরে এসে পড়েছে। একটি লোক—ময়লা কাপড়-জামা সত্ত্বেও বোঝা যায়, রায়বংশের ছেলে, মাটিতে পড়ে আছে।
সুরেশ্বর দাঁড়িয়ে আছে—পিছন ফিরে সে দাঁড়িয়েছিল-তবু বোঝা যাচ্ছি সে ক্রুদ্ধ, এখনও তার ক্রোধ যায়নি। তাকে হাতে ধরে রেখেছে অর্চনা। দরজার মুখে একজন কালো চশমা পরা, একজন সুপুরুষ বয়স্ক লোক। কাঁপছেন তিনি। সুরেশ্বর বলছে-শোন কমলেশ্বর, দেবোত্তর সম্পত্তি দেবোত্তরই থাকবে, ও ভাঙতে আমি দেব না। হ্যাঁ, কুইনিকে আমি বিয়ে করেছিলাম, তাতে জাত আমার যায়নি। তাতে রায়বংশের—অন্ততঃ দেবেশ্বর রায়ের বংশের—কেউ নরকস্থ হবে না। রায়বংশ তাতে ধন্য হয়েছে। জীবনে যদি কোন পুণ্য করে থাকি, তবে ওই আমার শ্রেষ্ঠ পুণ্য। আমার বাড়ীতে তোমার গলা টিপে ধরে তোমার চিৎকার বন্ধ করতে হল, তাতে আমি দুঃখিত, কিন্তু একবিন্দু লজ্জা আমার হচ্ছে না, অনুশোচনাও আমার হচ্ছে না, কারণ তিনি আমার অতিথি, আমার এককালের বান্ধবী, তিনি সম্ভ্রান্ত মহিলা, তিনি দেশের সেবা করেন, তিনি উচ্চশিক্ষিতা, মর্যাদাময়ী, তাঁর তুমি অপমান করেছ।
সুলতা এবার পিছন থেকে ডাকলে-সুরেশ্বর!
চমকে উঠে সুরেশ্বর এবং অর্চনা তার দিকে ফিরল। সুরেশ্বর বললে—তুমি নেমে এসেছ সুলতা!
—হ্যাঁ। আমার দেরী হয়ে যাচ্ছে। আমি যাব। কিন্তু তুমি এ কি করছ?
—আমাকে মাফ কর সুলতা, কি বলে যে আমি মাফ চাইব তোমার কাছে, আমি খুঁজে পাচ্ছি না।
—না না। আমি বুঝতে পারছি, উনি বোধহয়
—ও অতি ইতর! আগে গাঁজা খেত। মাথা খারাপ।
—থাক থাক। চল, আমাকে পৌঁছে দাও, ফটক পর্যন্ত।
সুরেশ্বর বললে-চল, সেই ভাল। রায়বংশ অভিশপ্ত সুলতা। কাল তোমাকে অর্ধেকটা বলেছি, তাতে সব বলা হয় নি, সব শুনলে বুঝতে পারতে।
চলতে চলতেই সুলতা বললে—ভাল-মন্দ নিয়ে সংসার সুরেশ্বর! টেনে টেনে কথাটা বললে সুলতা। অব্যক্ত কথাটার মধ্যে অনেক কিছু রইল।
সুরেশ্বর বললে—নিশ্চয় সুলতা, নিশ্চয়। কিন্তু দুনিয়াতে উঁচু বেদীর উপর যারা দাঁড়ায়, তাদের ভালোত্ব যত উজ্জ্বল, মন্দত্ব তত কালো, ভয়ঙ্কর। ধর্ম আর সম্পদের চেয়ে উঁচু বেদী আর নেই। দুটো নিয়ে রায়বংশের রক্ত।
—থাক ও কথা এখন। একটু পর প্রায় গেটের কাছাকাছি এসে বললে—ওই কালো চশমা পরা উনি কে? তোমাকে রাজাভাই বলছিলেন!
এতক্ষণে হেসে সুরেশ্বর বললে —তোমার কানে তো ঠিক মানে নিয়ে পৌঁচেছে! উনিই ব্রজেশ্বরদা। অন্ধ হয়ে গেছেন।
—অন্ধ?
—হ্যাঁ, অন্ধ। সম্ভবতঃ রক্তদুষ্টি থেকে। যার উৎপত্তি—চুপ করে গেল সে।
নীরবেই লনটা অতিক্রম করে ফটকে এসে দাঁড়াল দুজনে। সুরেশ্বর বললে—ওই ট্যাক্সি নিয়ে আসছে লছমন! বোধহয় এত সকালে ট্যাক্সি পাচ্ছিল না।
ট্যাক্সিখানা এসে ফটকের সামনে দাঁড়াল। লছমন নেমে বললে-এতনা সবেরে ট্যাক্সি একো নেহি থা। উধার সে লে আয়া—
—ঠিক হ্যায়।
ট্যাক্সির দরজা খুলে দিলে সুরেশ্বর, সুলতা ভিতরে উঠে বসল। সুরেশ্বর বললে—অর্ধেক জবানবন্দী আমার শুনেছ সুলতা, বাকি অর্ধেকটা শোনাবার জন্যে সন্ধ্যেবেলা তোমাকে আসতে অনুরোধ জানাচ্ছি। কমলেশ্বরের কথায় তুমি রাগ করনি, সে আমি জানি!
সুলতা বললে-আসব। নিশ্চয় আসব। একটা নতুন কৌতূহল জেগেছে আমার। তুমি বলছিলে, তোমার শ্রেষ্ঠ পুণ্যের কথা। কুইনিকে তুমি—
—হ্যাঁ, তাকে আমি বিয়ে করেছিলাম। সে আমার শ্রেষ্ঠ পুণ্য! রায়বংশের সব থেকে বড় দেনাটা শোধ করব বলে। থেমে গেল সে। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আবার সে বললে-সন্ধ্যেবেলা সব বলব সুলতা। চোখ অকস্মাৎ তার জলে ভরে উঠল, পিছন ফিরে সে বাড়ীর দিকে হন হন করে চলে গেল।