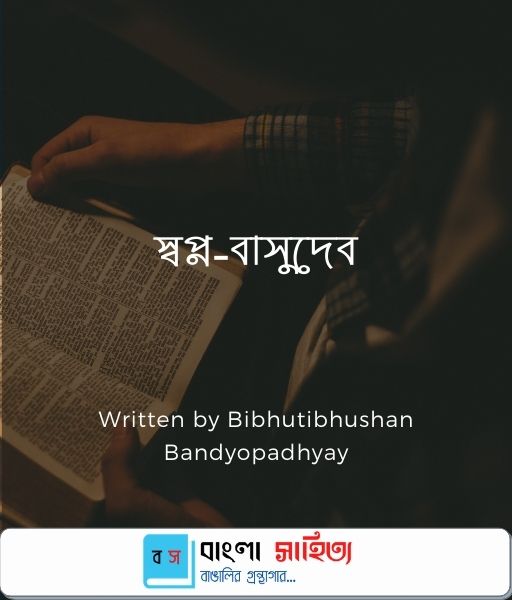আমার তখন বয়স নয় বছর। গ্রামের উচ্চ-প্রাইমারি স্কুলে পড়ি এবং বয়সের তুলনায় একটু বেশি পরিপক্ক। বিনু একদিন ক্লাসে একখানা বই আনিল, ওপরে সোনালিফুল হাতে একটি মেয়ের ছবি (ত্রিশ বছর আগেকার কথা বলিতেছি মনে রাখিবেন), রাঙা কাগজের মলাট, বেশি মোটা নয়, আবার নিতান্ত চটি বইও নয়।
আমি সেই বয়সেই দু-একখানা সুগন্ধি তেলের বিজ্ঞাপনের নভেল পড়িয়া ফেলিয়াছি; পূর্বেই বলি নাই যে বয়সের তুলনায় আমি একটু বেশি পাকিয়াছিলাম! সেজন্য বিনু আমাকে ক্লাসের মধ্যে সমঝদার ঠাওরাইয়া বইখানি আমার নাকের কাছে উঁচাইয়া সগর্বে বলিল, “এই দ্যাখো, আমার দাদা এই বই লিখেছেন, দেখেছিস?”
বলিলাম, “দেখি কী বই?”
মলাটের ওপরে লেখা আছে ‘প্রেমের তুফান’। হাতে লইয়া দেখিলাম, লেখকের নাম, শ্রীভূষণচন্দ্র চক্রবর্তী। দিনাজপুর, পীরপুর হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত, দাম আট আনা।
“তোর দাদার লেখা বই, কীরকম দাদা?”
বিনু সগর্বে বলিল, “আমার বড়োমামার ছেলে, আমার মামাতো ভাই।”
এই সময় নিতাই মাস্টার মহাশয় ক্লাসে ঢোকাতে আমাদের কথা বন্ধ হইয়া গেল। নিতাই মাস্টার আপন মনে থাকিতেন, মাঝে মাঝে কী এক ধরনের অসংলগ্ন কথা বলিতেন আর আমরা মুখ-চাওয়াচাওয়ি করিয়া হাসিতাম। জোরে হাসিবার উপায় ছিল না তাঁর ক্লাসে।
অমনি তিনি বলিয়া বসিতেন, “এই তিনকড়ি, এদিকে এসো, হাসছ কেন? ছানা চার আনা সের, কেরোসিন তেল ছ-পয়সা বোতল—”
এইসব মারাত্মক ধরনের মজার কথা শুনিয়াও আমাদের গম্ভীর হইয়া বসিয়া থাকিতে হইবে, হাসিয়া ফেলিলেই মার খাইয়া মরিতে হইবে।
বর্তমানে নিতাই মাস্টার ক্লাসে ঢুকিয়াই বলিলেন, “ও-খানা কী বই নিয়ে টানাটানি হচ্ছে সব? তিনটের গাড়ি কাল এসেছিল তিনটে পঁচিশ মিনিটের সময়, পঁচিশ মিনিট লেট—অমুক বিস্কুট পয়সায় দশখানা—”
আমরা হাসি অতিকষ্টে চাপিয়া মেঝের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বসিয়া রহিলাম।
নিতাই মাস্টার বইখানা হাতে লইয়া বলিলেন, “কার বই?”
বিনু সগর্বে বলিল, “আমার বই, স্যার। আমার দাদা লিখেছেন, আমাদের একখানা দিয়েছেন—”।
নিতাই মাস্টার বইখানা নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিয়া বলিলেন, “হু, থাক, একটু পড়ে দেখব।”
পরের দিন বইখানা ফেরত দিবার সময় মন্তব্য করিলেন, “লেখে ভালো, বেশ বই। ছোকরা এর পর উন্নতি করবে।”
বিনু বাধা দিয়া বলিল, “ছোকরা নন স্যার তিনি, আপনাদের বয়সি হবেন—”
নিতাই মাস্টার ধমক দিয়া বলিলেন, “বেশি কথা কইবে না, চুপ করে বসে থাকবে। আমার কথার ওপর কথা! পুরোনো তেঁতুলে অম্বলের ব্যথা সারে, আশ্বিন মাসে দুর্গাপুজো হয়।”
পুরোনো তেঁতুলে অম্বলের ব্যথা সারুক আর নাই সারুক, নিতাই মাস্টারের সার্টিফিকেট শুনিয়া বিনুর দাদার বইখানা পড়িবার অত্যন্ত কৌতূহল হইল; বিনুর নিকট যথেষ্ট সাধ্যসাধনা করিয়া সে-খানা আদায় করিলাম। বাড়িতে বাবা ও বড়োদার চক্ষু এড়াইয়া বইখানাকে শেষ করিয়া বিনুর এই অদেখা দাদাটির প্রতি মনে মনে ভক্তিতে আপ্লুত হইয়া গেলাম। একটি মেয়েকে কী করিয়া দুষ্ট লোক ধরিয়া লইয়া গেল, নানা কষ্ট দিল, অবশেষে মেয়েটি কীভাবে জলে ডুবিয়া মরিল, তাহারই অতিমর্মন্তুদ বিবরণ। পড়িলে চোখে জল রাখা যায় না।
কয়েক মাস কাটিয়া গিয়াছে, একদিন বিনু বলিল, “জানিস পাঁচু, আমার সেই দাদা, যিনি লেখক, তিনি এসেছেন কাল আমাদের বাড়ি।”
অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিলাম, “কখন এসেছেন? এখনও আছেন?”
“কাল রাতের ট্রেনে এসেছেন, দু-তিনদিন আছেন।”
“সত্যি? মাইরি বল—”
“মা-ইরি, চল বরং, আয় আমাদের বাড়ি।’
আমার ন-দশ বত্সর বয়সে ছাপার বই কিছু কিছু পড়িয়াছি বটে, কিন্তু যাহারা বই লেখে তাহারা কীরূপ জীব কখনো দেখি নাই। একজন জীবন্ত গ্রন্থকারকে স্বচক্ষে দেখিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না, বিনুর সহিত তাহার বাড়ি গেলাম।
বিনুদের ভেতর-বাড়িতে একজন একহারা কে বসিয়া বিনুর মার সঙ্গে গল্প করিতেছিল, বিনু দূর হইতে দেখাইয়া বলিল, ‘উনিই’। আমি কাছে যাইতে ভরসা পাইলাম না। সম্ভমে আপ্লুত হইয়া দূর হইতে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিলাম। লোকটি একহারা, শ্যামবর্ণ, অল্প দাড়ি আছে, বয়সে নিতাই মাস্টারের চেয়ে বড়ো হইবে তো ছোটো নয়, খুব গম্ভীর বলিয়াও মনে হইল। লোকটি সম্প্রতি কাশী হইতে আসিতেছে, বিনুর মায়ের কাছে সবিস্তারে সেই ভ্রমণকাহিনিই বলিতেছিল। প্রত্যেক কথা আমি গিলিতে লাগিলাম ও হাত-পা নাড়ার প্রতি ভঙ্গিটি কৌতূহলের সহিত লক্ষ করিতে লাগিলাম।
লেখকরা তাহা হইলে এইরকম দেখিতে।
সেইদিনই গ্রামে বেশ একটা সাড়া পড়িয়া গেল, বিনুর বাবা মুখুজ্যেদের চণ্ডীমণ্ডপে গল্প করিয়াছেন, তাঁহার বড়ো শালার ছেলে বেড়াইতে আসিয়াছে, মস্ত একজন লেখক, তার লেখার খুব আদর। ফলে গ্রামের লোক দলে দলে দেখা করিতে চলিল। বিনুর মা মেয়েমহলে রাষ্ট্র করিয়া দিলেন, ‘প্রেমের তুফানে’-র লেখক তাদের বাড়ি আসিয়াছেন। উক্ত বইখানি ইতিমধ্যে পুরুষেরা যত পড়ুক আর না-পড়ক, গ্রামের মেয়েমহলে হাতে হাতে ঘুরিয়াছে খুব, অনেক মেয়ে পড়িয়া ফেলিয়াছে, বিনুর মা ভ্রাতুস্পুত্রগর্বে স্ফীত হইয়া নিজে যাচিয়াও অনেককে পড়াইয়াছেন, সুতরাং মেয়েমহলও ভাঙিয়া আসিল একজন জলজ্যান্ত লেখককে দেখিবার জন্য। বিনুদের বাড়ি দিনরাত লোকের ভিড়; একদল যায়, আর একদল আসে। অজ পাড়াগাঁ, এমন একজন মানুষের—যার বই ছাপার অক্ষরে বাহির হইয়াছে, দেখা পাওয়া আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়ার মতোই দুর্লভ।
ক-দিন কী খাতির এবং সম্মানটাই দেখিলাম বিনুর দাদার! এর বাড়ি নিমন্ত্রণ, ওর বাড়ি নিমন্ত্রণ, বিনুর মা সগর্বে মেয়েমহলে গল্প করেন, “বাছা এসে ক-দিন বাড়ির ভাত মুখে দিলে? নেমন্তন্ন খেতে খেতেই ওর প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠেছে—’
ভাবিলাম—সত্যি, সার্থক জীবন বটে বিনুর দাদার! লেখক হওয়ার সম্মান আছে।
ভূষণদার সহিত এইভাবে আমার প্রথম দেখা।
অত অল্প বয়সে অবশ্য ভূষণদাদার নিকটে ঘেঁষিবার পাত্তা পাই নাই—কিন্তু বছর দুই পরে তিনি যখন আবার আমাদের গ্রামে আসিলেন, তখন তাঁহার সহিত মিশিবার অধিকার পাইলাম—যদিও এমন কিছু ঘনিষ্ঠভাবে নয়। তিনি যে মাদৃশ বালকের সঙ্গে কথা কহিলেন, ইহাতেই নিজেকে ধন্য মনে করিয়া বাড়ি গিয়া উত্তেজনায় রাত্রে ঘুমাইতে পারিলাম না।
সে-কথাও অতিসাধারণ ও সামান্য। দাঁড়াইয়া আছি দেখিয়া ভূষণদাদা বলিয়াছিলেন, “তোমার নাম কী হে? তুমি বুঝি বিনুর সঙ্গে পড়ো?”
শ্রদ্ধা ও সমজড়িত কণ্ঠে উত্তর করিলাম, “আজ্ঞে হ্যাঁ।”
“কী নাম তোমার?”
“শ্রীপাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়।”
“বেশ।”
কথা শেষ হইয়া গেল। দুরু দুরু বক্ষে বাড়ি ফিরিয়া আসিলাম। প্রথম দিনের পক্ষে এই-ই যথেষ্ট। পরদিন আরও ভালো করিয়া আলাপ হইল। নদীর ধারে বিনু, আমি, আরও দু-একটি ছেলে তাঁর সঙ্গে বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলাম। ভূষণদাদা বলিলেন, “বলো তো বিনু, ‘এ দম্ভোলি বৃত্রাসুর শিরচ্ছিন্ন যাহে’—দম্ভোলি মানে কী? পারলে না? কে পারে?”
পূর্বেই বলিয়াছি, আমি বয়সের তুলনায় পাকা ছিলাম। তাড়াতাড়ি উত্তর করিলাম, “আমি জানি, বলব…বর্জ।”
“বেশ বেশ, কী নাম তোমার?”
কালই নাম বলিয়াছি; এ দীনজনের নাম তিনি মনে রাখিয়াছেন, এ আশা করাও আমার মতো অর্বাচীন বালকের পক্ষে ধৃষ্টতা। সুতরাং আবার নাম বলিলাম।
“বেশ বাংলা জানো তো! বই-টই পড় নাকি?”
এ সুযোগ ছাড়িলাম না, বলিলাম, “আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনার বই সব পড়েছি।”
বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, ইতিমধ্যে ভূষণদার আরও দুইখানি উপন্যাস ও একখানি কবিতার বই বাহির হইয়াছিল—বিনুদের বাড়ি সেগুলিও আসিয়াছিল; বিনুর নিকট হইতে আমি সবগুলিই পড়িয়াছিলাম।
ভূষণদাদা বিস্ময়ের সুরে বলিলেন, “বলো কী? সব বই পড়েছ? নাম করো তো?”
“প্রেমের তুফান, বেণুর বিয়ে, কমলকুমারী আর দেওয়ালি।”
“বাঃ বাঃ, এ যে বেশ দেখছি। কী নাম বললে?”
বিনীতভাবে পুনরায় নিজের নাম নিবেদন করিলাম।
“বেশ ছেলে। দ্যাখ তো বিনু, তোর চেয়ে কত বেশি জানে!”
গর্বে আমার বুক ফুলিয়া উঠিল। একজন লেখক আমার প্রশংসা করিয়াছেন। তারপর ভূষণদাদা (বিনুর সুবাদে আমিও তাঁহাকে তখন ‘দাদা’ বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছি) নবীন সেন এবং হেমচন্দ্রের কবিতা আবৃত্তি করিয়া শুনাইলেন। সাহিত্য, কবিতা এবং তাঁহার নিজের রচনা সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন; তার কতক বুঝিলাম কতক বুঝিলাম না—এগারো বছরের ছেলের পক্ষে সব বোঝা সম্ভব ছিল না।
বছরের পর বছর কাটিয়া গেল। আমি হাইস্কুলে ভর্তি হইলাম। একদিন ভূষণদাদা সম্বন্ধে আমি এক বিষম ধাক্কা খাইলাম আমাদের স্কুলের বাংলা মাস্টারের নিকট হইতে। কী উপলক্ষ্যে মনে নাই, মাস্টারমশায় আমাদের ক্লাসের ছেলেদের জিজ্ঞাসা করিলেন, “বাংলার দেশের আরও দু-একজন বড়ো লেখকের নাম করতে
কে পারে?”
একজন বলিল, ‘নবীনচন্দ্র,’ একজন বলিল, ‘সুরেন ভটচাজ’ (তখনকার কালে মস্ত নাম), একজন বলিল, ‘রজনি সেন’ (তখন সবে উঠিতেছেন)—আমি একটু বেশি জানিবার বাহবা লইবার জন্য বলিলাম—’ভূষণচন্দ্র চক্রবর্তী।‘
মাস্টারমশায় বলিলেন, “কে?”
“ভূষণচন্দ্র চক্রবর্তী। আমি পড়েছি তাঁর সব বই, আমার সঙ্গে আলাপ আছে।”
“সে আবার কে?”
আমি মাস্টারমশায়ের অজ্ঞতা দেখিয়া অবাক হইলাম।
“কেন ভূষণচন্দ্র চক্রবর্তী খুব বড়ো লেখক–প্রেমের তুফান, কমলকুমারী, দেওয়ালি, বেণুর বিয়ে—এইসব বইয়ের—”।
মাস্টারমশায় হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, ক্লাসের ছেলেদের বেশিরভাগই না-বুঝিয়া সে হাসিতে যোগ দিল। উহাদের সম্মিলিত হাসির শব্দে ক্লাসরুম ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম হইল।
আমার কান গরম হইয়া উঠিল, রীতিমতো অপদস্থ বিবেচনা করিলাম নিজেকে। কেন, ভূষণদাদা বড়ো লেখক নন? বা রে!
মাস্টারমশায় বলিলেন, “তোমার গাঁয়ের আত্মীয় বলে আর তোমার সঙ্গে আলাপ আছে বলেই তিনি বড়ো লেখক হবেন তার কী মানে আছে? কে তাঁর নাম জানে? ওরকম বলো না।’
ভূষণদাদার সাহিত্যিক যশ ও খ্যাতি সম্বন্ধে আমি এ পর্যন্ত কেবল একতরফা বর্ণনাই শুনিয়া আসিয়াছি বিনুর মায়ের মুখে, বিনুর বাবার মুখে, ভূষণদাদার নিজের মুখে। তাহাই বিশ্বাস করিয়াছিলাম, সরল বালক মনে। এই প্রথম আমার তাহার উপর সন্দেহের ছায়াপাত হইল।
এতদিন গাঁয়ে থাকিয়া কেবল সুগন্ধি তেলের বিজ্ঞাপনের নভেলই পড়িয়াছি— ক্রমে স্কুল লাইব্রেরি হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের ও আরও অন্যান্য বড়ো লেখকের বই লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিলাম। বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে ভালো মন্দ বুঝিবার ক্ষমতাও জন্মিল—ফলে বছর চার-পাঁচ স্কুলে পড়িবার পরে আমার উপরে ভুষণচন্দ্র চক্রবর্তীর প্রভাব যে অত্যন্ত ফিকে হইয়া দাঁড়াইবে, ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার।
আমি যে-বার ম্যাট্রিক পাস করিয়া কলেজে ভর্তি হইয়াছি, সে-বার শ্রাবণ মাসে বিনুর ভগ্নীর বিবাহ উপলক্ষ্যে ভূষণদাদা আবার আমাদের গ্রামে আসিলেন। তখন আমার চোখে তিনি আর ছেলেবেলার সে বড়ো লেখক ভূষণচন্দ্র নন, বিনুর ভূষণদাদা, সুতরাং আমারও ভূষণদাদা। তখন বেশ সমানে সমানে কথাবার্তা। বলিলাম, দাদারও আর সে মুরুব্বিয়ানা চাল নাই, থাকিবার কথাও নয়। তিনিও সমানে সমানেই মিশিলেন।
একখানা বই দেখিলাম, বিবাহ-বাটীর কুটুম্বসাক্ষাৎদের হাতে হাতে ঘুরিতেছে, কবিতার বই, নাম—’প্রতিমা-বিসর্জন’। দ্বিতীয় পক্ষের পত্নীর মৃত্যুতে শোকোচ্ছাস প্রকাশ করিয়া ভূষণদাদা কবিতা লিখিয়া বই ছাপাইয়াছেন বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।
বিনুও তো আর বাল্যের সেই বিনু নাই। সে বলিল—”মজার কথা শোন, আগের বউদিদি ষোলো বছর ঘর করে ছেলেপুলের মা হয়ে মরে গেল বেচারি, তার বেলা শোকের কবিতা বেরুল না। দ্বিতীয় পক্ষের বউদি—দু-তিন বছর ঘর করে ডবকা বয়সেই মারা গেল—দাদার তাই শোকটা বড্ড লেগেছে—একেবারে। প্রতিমা—বি স র্জ-ন!”
ভূষণদাদা আমাকেও একখানা বই দিয়াছিলেন, দু-তিন দিন পরে আমায় বলিলেন, “প্রতিমা-বিসর্জন কেমন পড়লে হে?”
অতিসাধারণ ধরনের কবিতা বলিয়া মনে হইলেও বলিলাম, “বেশ চমৎকার!’’ ভূষণদাদা উৎসাহের সহিত বলিলেন, “বাংলা দেশে ‘উদভ্রান্ত-প্রেম’-এর পরে আমার মনে হয়, এ ধরনের বই আর বেরোয়নি। নিজের মুখে নিজের কথা বলছি বলে কিছু মনে কোরো না-তবে তোমাদের ছোটো দেখেছি, তোমাদের কাছে বলতে দোষ নেই।”
ভূষণদাদার দাড়ি চুলে বেশ পাক ধরিয়াছে, তাঁহাকে সমীহ করিয়া চলি, সুতরাং প্রতিবাদ না-করিয়া চুপ করিয়া গেলাম। যদিও ‘উদ্ভান্ত-প্রেম’-এর প্রতি আমার যে খুব শ্রদ্ধা ছিল তাহা নয়, তবুও ভূষণদাদার কথা শুনিয়া সমলোচনা-শক্তির প্রতি বিশ্বাস হারাইলাম।
ভূষণদাদার আর্থিক অবস্থা খুব ভালো নয়, অনেকদিন হইতেই জানি। তিনি ক্যাম্বেল স্কুল হইতে ডাক্তারি পাস করিয়া দিনাজপুরের এক সুদূর পল্লিগ্রামে জমিদারদের দাতব্যচিকিৎসালয়ে চাকুরি করিতেন, স্বাধীন ব্যাবসা কোনোদিন করেন নাই।
এবার শুনিলাম ভূষণদাদার সে চাকুরিটাও যায় যায়। বিনুই এ সংবাদ দিল।
ভূষণদাদা আসার পরদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, “ওহে, তোমরা তো কলকাতায় ছাত্রমহলে ঘোরো, পাঁচটা কলেজের ছাত্রদের সঙ্গে দেখা হয়, ছাত্রমহলে আমার
বই সম্বন্ধে কী মতামত কিছু শুনেছ?” |||||||||| হঠাৎ বড়ো বিব্রত হইয়া পড়িলাম, আমতা আমতা সুরে বলিলাম, “আজ্ঞে হ্যাঁ—তা বেশ ভালোই—’
বলেন কী ভূষণদাদা! বিব্রত ভাবটা কাটিয়া গিয়া এবার আমার হাসি পাইল। কলকাতায় ছাত্রমহলে ভূষণ চক্রবর্তী নামই কেউ জানে না, তার বই পড়া! আর সে সম্বন্ধে মতামত।
ভূষণদাদা উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, “কী কী, কীরকম বলে? আমার কোন বইটার কথা শুনেছ? পাষাণপুরী না দেওয়ালি?”
অকূলে কূল পাইলাম। ভূষণদাদার বইয়ের নাম কী আমার একটাও মনে ছিল ছাই! বলিলাম, “হ্যাঁ, ওই পাষাণপুরীর কথাই যেন শুনেছি।”
ভূষণদাদা আর আমায় ছাড়িতে চান না। কী শুনিয়াছি, কোথায় শুনিয়াছি, কাহার কাছে শুনিয়াছি? পাষাণপুরী তাঁর উপন্যাসগুলির মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট। তবুও তো তিনি পাবলিশার পান নাই, সব বই-ই নিজে ছাপাইয়াছেন, দিনাজপুরের অজ পাড়াগাঁয়ে বসিয়া বই বিক্রি ও বিজ্ঞাপনের কোনো সুবিধা করিতে পারেন নাই।
বিনু আমায় আড়ালে বলিল, “এই অবস্থা, পঞ্চাশটি টাকা মাইনে পান ডাক্তারি করে, সংসারই চলে না, তা থেকে খরচ করেন ওইসব বাজে বই ছাপতে। ভূষণদাদার চিরকালটা একরকম গেল। বাতিক যে কতরকমের থাকে!”
ইহার পর আরও ছ-সাত বছর কাটিয়া গেল।
আমি পাস করিয়া বাহির হইয়া নানারকম কাজকর্ম করি এবং সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু লিখিও।
ভুষণদাদার প্রভাব আমার জীবন হইতে সম্পূর্ণ যায় নাই, মনের তলে কোথায়। চাপা ছিল, লেখক হওয়া একটা মস্ত বড়ড়া কিছু বুঝি! সেই যে আমাদের গ্রামে বাল্যকালে সেবার ভূষণদাদাকে সম্মান পাইতে দেখিয়াছিলাম, সেই হইতেই বোধ হয় লেখক হওয়ার সাধ মনে বাসা বাঁধিয়া থাকিবে, কে জানে?
আমার লেখকজীবন যখন পাঁচ-ছ বছরের পুরাতন হইয়া পড়িয়াছে, দু-চারখানা ভালো মাসিক পত্রিকায় লেখা প্রায়শ বাহির হয়, কিছু কিছু আরও হইতেছে, সে সময় কী একটা ছুটিতে দেশে গেলাম। বিনুদের বাড়িতে গিয়া দেখি, ভূষণদাদা অসুস্থ অবস্থায় সেখানে সপরিবারে কিছুদিন হইতে আছেন। আমায় বলিলেন, “পাঁচু, শুনলাম আজকাল লিখছ? কোন কোন কাগজে লেখা বেরিয়েছে?”
কাগজগুলির কয়েকখানি আমার সঙ্গেই ছিল, ইতিমধ্যে গ্রামের অনেকেই সেগুলি দেখিয়াছে। ভুষণদাদাকেও দেখাইলাম—দেখাইয়া বেশ একটু গর্ব অনুভব করিলাম।
ভূষণদাদা কাগজ ক-খানা উলটাইয়া দেখিয়া বলিলেন, “এইসব কাগজে লিখছ? বেশ বেশ। এসব তো বেশ নাম-করা পত্রিকা। একটু ধরাধরি করতে হয়, না? তুমি কাকে ধরেছিলে? একটু ধরাধরি না-করলে আজকাল কিছুই হয় না। গুণের আদর কী আর আছে? এই দেখো না কেন, আমি পাড়াগাঁয়ে থাকি বলে নিজেকে পুশ করতে পারলাম না। আমার ‘নারদ’-কাব্য পড়োনি? দু-বছর ধরে খেটে লিখেছি, প্রাণ দিয়ে লিখেছি। কিন্তু হলে হবে কী, ওই ধরাধরির অভাবে বইখানা নাম করতে পারছে না।”
বৈকালে নদীর ধারে বসিয়া ভূষণদাদার মুখে তাঁহার ‘নারদ’-কাব্যের অনেক ব্যাখ্যা শুনিলাম। অমিত্রাক্ষর ছন্দ হইলেও তাহার মধ্যে নিজস্ব জিনিস কী একটা ঢুকাইয়া দিয়াছেন ভূষণদাদা, অমন দার্শনিকতা আধুনিক কোনো বাংলা গ্রন্থে নাই, এ কথা তিনি জোর করিয়া বলিতে পারেন।
বলিলাম, “বইখানা ছেপেছে কারা?”
“আমিই ছেপেছি। লোকের দোরে দোরে বেড়িয়ে ছাপানোর জন্যে খোশামোদ করা—ওসব আমার দ্বারা হবে না।”
মনে হইল ভূষণদাদা আমারই প্রতি যেন বক্রকটাক্ষ করিতেছেন এইসব উক্তি দ্বারা। যাহা হউক, কিছু না-বলিয়া চুপ করিয়া রহিলাম।
বছরখানেক পরে আমি আমার কর্মস্থলে একটা বুকপোস্ট পাইলাম। খুলিয়া দেখি, ভূষণদাদা সেই ‘নারদ’-কাব্যখানি আমায় পাঠাইয়াছেন, সঙ্গে একখানা বড়ো চিঠি। ‘নারদ’-কাব্যখানির উচ্চ প্রশংসা করিয়া বহুলোক ইতিমধ্যে চিঠি লিখিয়াছেন। চিঠিগুলি তিনি পুস্তিকাকারে ছাপিয়া ওই সঙ্গে আমায় পাঠাইয়াছেন। আমি যেন কলিকাতার কোনো নামকরা কাগজে বইখানির ভালো ও বিস্তৃত সমালোচনা বাহির করিয়া দিই, এই ভূষণদাদার অনুরোধ।
ছাপানো প্রশংসাপত্রগুলি পড়িয়া আমার খুব ভক্তি হইল না। একজন মফসসলের কোন শহরের প্রধান ডাক্তার লিখিয়াছেন, কবি নবীনচন্দ্রের ‘রৈবতক’ কাব্যের পরে আর একখানি উৎকৃষ্ট কাব্য আবার বাংলা সাহিত্যে বাহির হইল বহুকাল পরে। আর একজন কোথাকার প্রধান উকিল লিখিতেছেন, কে বলে বাংলা ভাষার দুর্দিন? বাংলা সাহিতের দুর্দিন? যে দেশে আজও ‘নারদ’-কাব্যের মতো কাব্য রচিত হয়ে থাকে (মনে ভাবিলাম, ভদ্রলোক কী বাংলা কবিতার কিছুই পড়েন নাই?), সে দেশে, ইত্যাদি ইত্যাদি।
মন দিয়া ‘নারদ’-কাব্য পড়িলাম। নবীনচন্দ্রের ‘বৈবতক’-এর ব্যর্থ অনুকরণ। লম্বা লম্বা বক্তৃতা—মাঝে মাঝে ‘ভূমা’, ‘প্রপঞ্চ,’ ‘ক্ষর’, ‘অক্ষর,’ ‘শাশ্বত’, ‘অব্যয়’ প্রভৃতি শব্দের ভীষণ ভীড়—ইহাকে ‘নারদ’-কাব্য না-বলিয়া গীতা বা শ্রীমদ্ভাগবতের পদ্যে ব্যাখ্যা বলিলেও চলিত।
আমি চিঠির উত্তরে লিখিলাম, ‘নারদ’, বেশ লাগিয়াছে, তবে কলিকাতার কোনো নামকরা মাসিক পত্রিকায় ইহার বিস্তৃত সমালোচনা বাহির করা আমার সাধ্যায়ত্ত নয়। সে চিঠির উত্তরে ভূষণদাদা আমায় আরও দুই-তিনখানি পত্র লিখিলেন—যদি বইখানি আমার ভালো লাগিয়া থাকে, তবে সে-কথা ছাপাইয়া প্রকাশ করিবার সৎসাহস থাকা আবশ্যক ইত্যাদি। সে-সব চিঠির উত্তর দিলাম না।
ইহার বছরখানেক পরে আমি আমার বিদেশের কর্মস্থান হইতে কলিকাতায় আসিয়াছি। শ্রাবণ মাস, তেমনি বর্ষা আরম্ভ হইয়াছে। দিনেরাত্রে বৃষ্টির বিরাম নাই। এ-বেলা একটু ধরিয়াছে বলিয়াই বাহির হইয়াছি। গোলদিঘির কাছাকাছি আসিয়া একখানা হ্যান্ডবিল হাতে পড়িল। হ্যান্ডবিলখানা ফেলিয়া দেওয়ার পূর্বে অন্যমনস্কভাবে সে-খানার উপর একটু চোখ বুলাইয়া লইতে গিয়া দস্তুরমতো বিস্মিত ও উত্তেজিত হইয়া উঠিলাম। উহাতে লেখা আছে—
‘নারদ’-কাব্যের খ্যাতনামা কবি
বঙ্গভারতীর কৃতী সন্তান
শ্রীযুক্ত ভূষণচন্দ্র চক্রবর্তীকে (বড়ো বড়ো অক্ষরে)
সংবর্ধনা করিবার জন্য কলিকাতাবাসীগণের
জনসভা (আধইঞ্চি লম্বা অক্ষরে)
স্থান-ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হল, সময় সন্ধ্যা ৬ টা।
সভাপতিত্ব করিবেন
একজন খ্যাতনামা নামজাদা প্রবীণ সাহিত্যিক।
ব্যাপার কী? চক্ষুকে যেন বিশ্বাস করিতে পারিলাম না—ভূষণদাদাকে সংবর্ধনা করিবার জন্য কলিকাতাবাসীগণ (কী ভয়ানক ব্যাপার!) জনসভা আহ্বান করিয়াছেন ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে অতবড়ো নামজাদা সাহিত্যিকের সভাপতিত্বে! কই ‘নারদ’-কাব্যের এতাদৃশ জনপ্রিয়তা তো পূর্বে মোটেই শুনি নাই? যাহা হউক, হইলে খুব ভালো কথা, কিন্তু কলিকাতাবাসীগণ কী ক্ষেপিয়া গেল হঠাৎ?
হ্যান্ডবিলের তারিখ লক্ষ করিয়া দেখিলাম, সেই দিনই সন্ধ্যাবেলা সভা। সাড়ে ছ-টার বেশি দেরি নাই, যদি লোকের খুব ভিড় হয়, পৌঁনে ছটায় ইনস্টিটিউটে গিয়া ঢুকিলাম। তখনও কেহ আসে নাই—অতবড়ো হল একেবারে খালি। এক পাশে গিয়া বসিলাম। ছ-টা বাজিল, জনপ্রাণীরও দেখা নাই—এই সময় আবার জোরে বৃষ্টি নামিল, সওয়া ছ-টা— কেহই নাই, সাড়ে ছটার দু-এক মিনিট পূর্বে দেখি ভূষণদাদা অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে একতাড়া কাগজ বগলে হলে প্রবেশ করিতেছেন, পিছনে চার পাঁচটি ভদ্রলোক—তাঁহাদের কাহাকেও চিনি না। তখন সভার সাফল্য সম্বন্ধে আমার ঘোর সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, এ অবস্থায় ভূষণদাদার সহিত দেখা করিলে তিনি অপ্রতিভ হইতে পারেন—সুতরাং হলের বাহিরে গা-ঢাকা দিয়া রহিলাম।
পৌঁনে সাতটা—জনপ্রাণী না, সভাপতিও অনুপস্থিত। সাতটা, তথৈবচ। এমন জনশূন্য জনসভা যদিও-বা কখনো দেখিয়াছি! ভূষণদাদার অবস্থা দেখিয়া বড়ো কষ্ট হইল। তিনি ও তাঁহার সঙ্গের ভদ্রলোক কয়জন কেবল ঘর-বাহির করিতেছেন, নিজেদের মধ্যেই উত্তেজিত ভাবে কী পরামর্শ করিতেছেন—আবার একবার করিয়া ইনস্টিটিউট-এর গেটের কাছে যাইতেছেন। সওয়া সাতটা—কাকস্য পরিবেদনা। সাড়ে সাতটা—পূর্ববৎ অবস্থা। কলিকাতাবাসীগণের জনসভায় কলিকাতাবাসীগণই আসিতে ভুলিয়া গেলেন কেমন করিয়া!
পৌঁনে আটটার সময় ভূষণদাদা সঙ্গীদের লইয়া বাহির হইয়া গেলেন—অল্পক্ষণ পরে আমিও হল পরিত্যাগ করিলাম।
পরদিন বিনুর মেলোমশায় তারিণীবাবুর সঙ্গে দেখা। তিনি আমাকে চেনেন খুব ভালোই বিনুর সঙ্গে কতবার সিমলা স্ট্রিটে তাঁর বাড়িতে গিয়াছি। কুশল প্রশ্নাদির পরে তিনি বলিলেন, “ভূষণ যে এখানে এসেছে হে, আমার বাসাতেই আজ আট দশ দিন আছে। কী একখানা বই নিয়ে খুব ঘোরাঘুরি করছে। ওর মাথা আর মুণ্ডু। এদিকে এই অবস্থা, সতেরো-আঠারো বছরের মেয়ে একটা, পনেরো বছরের
মেয়ে একটা—পার করবে কোথা থেকে তার সংস্থান নেই—আবার কাল দেখি নিজের পয়সায় একগাদা কী মিটিং না ফিটিং-এর হ্যান্ডবিল ছেপে এনেছে। আর বলো কেন, একেবারে মাথা খারাপ!”
বলিলাম, “হ্যাঁ-হ্যাঁ, দেখেছিলুম বটে একখানা হ্যান্ডবিলে—জনসভা না কী—”
— “জনসভা না ওর মুণ্ড! ও নিজেই তো পরশু দুপুরে বসে বসে ওখানা লিখলে! আমার বাড়িতে দুজন বেকার ভাইপো আছে, তাদের নিয়ে কোথায় সব ঘুরছে ক দিন দেখতে পাই—সাড়ে সতেরো টাকা প্রেসের বিল কাল দিলে দেখলাম আমার সামনে—এদিকে শুনি, বাড়িতে নিতান্ত দুরবস্থা…অতবড়ো সব আইবুড়ো মেয়ে গলায়, এক পয়সার সংস্থান নেই—তার বিয়ে!”
মাঘ মাসের শেষে আমি কার্যোপলক্ষ্যে জলপাইগুড়ি যাইতেছি, পার্বতীপুর স্টেশনে দেখি, ভূষণদাদা একটি ব্যাগ হাতে প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করিতেছেন। আমি গিয়া প্রণাম করিতেই বলিলেন, “আরে পাঁচু যে! ভালো তো? সেই পশ্চিমেই আজকাল চাকুরি করো তো? কোথায় যাচ্ছ এদিকে?”
“আজ্ঞে একটু জলপাইগুড়িতে। আপনি কোথায়?”
“আমি একটু যাচ্ছি কলকাতায়। হ্যাঁ, তোমাকে বলি—শোনোনি বোধ হয়, আমার ‘নারদ’-কাব্যের খুব আদর হয়েছে। এর মধ্যে কলকাতায় ইনস্টিটিউট হলে প্রকাণ্ড সভা হয়ে গেল তাই নিয়ে। অমুকবাবু সভাপতি ছিলেন। খুব উৎসাহ দেখলাম লোকজনের মধ্যে, খুব ভিড়—দেখবে? এই দেখো।” বলিয়াই ভূষণদাদা ব্যাগ খুলিয়া জনসভায় ছাপানো হ্যান্ডবিল একখানা আমার হাতে দিয়া বলিলেন, “পড়ে দেখো।”