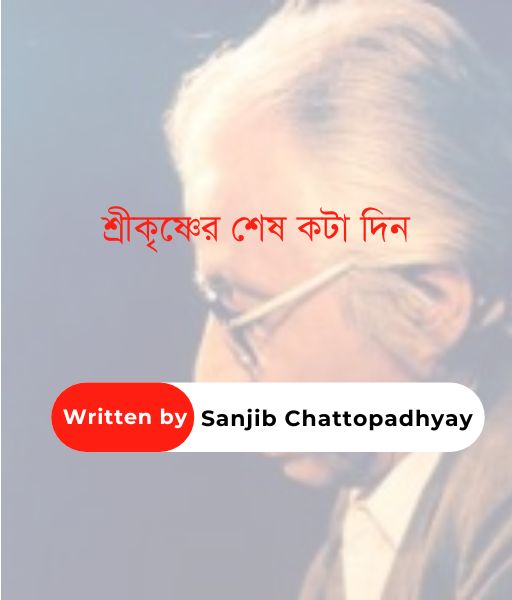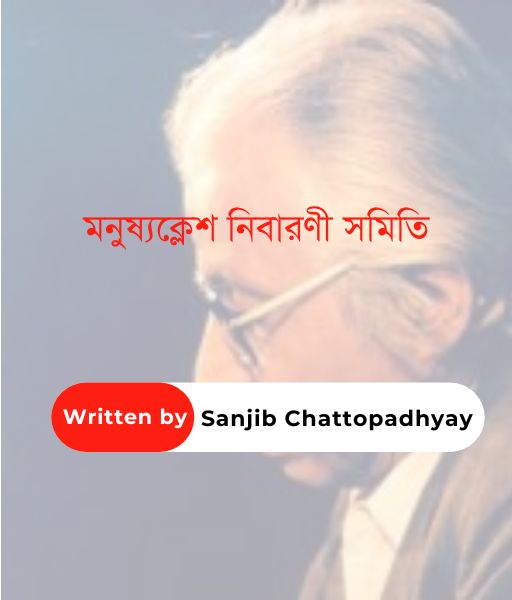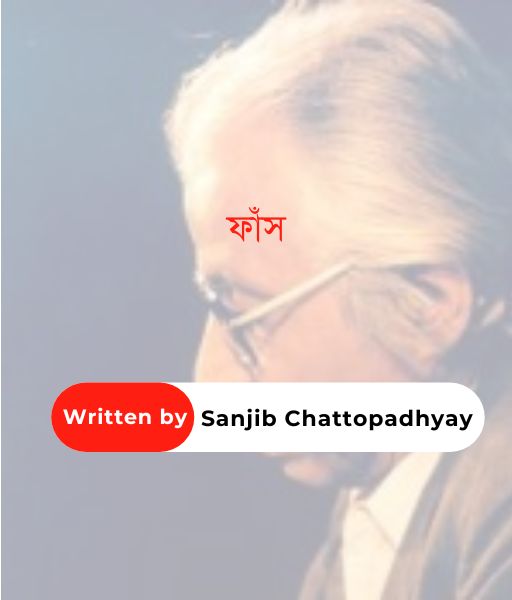বর্ধমানের রাজপরিবারের অভ্যুত্থান অলৌকিক
বসন্তকুমারী : বর্ধমানের রাজপরিবারের অভ্যুত্থান অলৌকিক। অনেকটা ইংরেজিতে যেমন বলে–From rags to reiches ছিল চটে শুয়ে, বসল গিয়ে সিংহাসনে। একে মিরাকল বলা যাবে না, সৎ প্রচেষ্ঠা এবং ভাগ্যের সংযোগ। মহামতী আকবর দিল্লির সিংহাসনে। স্বামীজি যে মোগলকে সবচেয়ে বেশি শ্রদ্ধা করতেন তিনি আকবর। ইংরেজরা আকবরকেই। বলেছেন–দ্য গ্রেট মোগল। ১৫৭৪ সালের বাংলা। শূর বংশের পাঠানদের রাজত্বকাল শেষ হওয়ার পর কররানি বংশের সুলেমান কররানি বাংলার সুলতান হয়েছিলেন ১৫৬৫ সালে। এই সুলেমান আকবরের শাসন কর্তৃত্বকে অস্বীকার করেননি। ফলে কোনও সমস্যার সৃষ্টি হয়নি। ১৫৭২ সালে তাঁর মৃত্যু হল। কনিষ্ঠপুত্র দাউদ খান সিংহাসনে বসলেন। সিংহাসনে বসেই মনে করলেন, আমি একটা কেউকেটা। দিল্লি অনেক দূরে। এই বাংলায় তারা দাঁত ফোঁটাতে আসবে না। সিংহাসনে বসেই তিনি এমন কয়েকটি কাজ করলেন যার ফল হল ভয়ংকর। প্রথম, নিজের নামে খুত বা পাঠ। দ্বিতীয়, নিজের নামে মুদ্রাও চালু করলেন। দিল্লির সিংহাসনে আকবর নড়ে বসলেন। তাঁর সুদক্ষ সেনাপতি মুনিম খাঁকে বাংলায় পাঠালেন। দাউদ খানকে ঢিট করতে। ১৫৭৬ সালের জুলাই মাস। রাজমহলের যুদ্ধক্ষেত্রে দাউদ খান মোগল সেনাদের মুখোমুখি হলেন। যথারীতি যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত। দাউদ খানের পরিবারবর্গ তখন বর্ধমান শহরে। তাঁরা বন্দি হলেন। রাজা টোডরমল বর্ধমান শহরেই ঘাঁটি গাড়লেন।
এরপরের দশ বছর দাউদের পুত্র কতলু খান বা কুট্টি খান আকবর বাদশার সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে চুক্তি অনুসারে কাজ করায় কোনও গোলযোগ নতুন করে তৈরি হয়নি। ওদিকে দিল্লির মসনদে পরিবর্তন দেখা দিল। আকবর প্রয়াত, সিংহাসনে জাহাঙ্গির। বাংলাদেশে আবার। বিদ্রোহ মাথা চাড়া দিল। ১৬২৪ খ্রিস্টাব্দ। যুবরাজ খুররাম, পরে দিল্লির বাদশাহ হয়ে শাহজাহান নামে পরিচিত হল। তিনি গড়ের দুর্গ এবং বর্ধমান শহর দখল করলেন। সেই সময় পাঞ্জাবের অন্তর্গত লাহোর কোটালির কাপুর ক্ষত্রিয় আবু রায় ভাগ্যের সন্ধানে মাতৃভূমি ছেড়ে চলে আসেন বর্ধমানে। শুরু করেন চিরস্থায়ী বসবাস। বর্ধমান রাজের প্রতিষ্ঠা শুরু হল। বলা চলে। পরবর্তীকালে মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ মোগল বাদশাহ শাহজাহানের প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতা জানালেন এইভাবে, আমি তাঁর কাছে ঋণী। কারণ তাঁর ঔদার্যে আমি এই জমিদারির মালিক হয়েছি। অবশ্যই উপযুক্ত জমিদার। তা না হলে সারা ভারতে মহারাজাধিরাজ বর্ধমান সর্বশ্রেষ্ঠ জমিদার হিসাবে স্বীকৃতি পেতেন না। দিল্লির কোষাগারে সবচেয়ে বেশি খাজনা জমা পড়ত বর্ধমান রাজের।
সঙ্গম রায় : বর্ধমান অঞ্চলের ক্ষত্রিয়দের আদি পুরুষ আর বর্ধমান রাজবংশের প্রথম রাজা। লাহোরের কোটলে মহল্লার অধিবাসী। তিনি শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করার জন্য পুরীতে আসেন। সেখান থেকে ফেরার সময় বর্ধমান শহরের কাছে বোলেরা বৈকুণ্ঠপুর অঞ্চলটি ভালো লেগে যায়। সেখানেই বসবাস শুরু করলেন। তিনি ছিলেন শিবভক্ত। প্রথমেই একটি শিবমন্দির স্থাপন করলেন যা আজও আছে। শের আফগানের সঙ্গে জাহাঙ্গিরের ভাই। কুতুবউদ্দিনের যুদ্ধের সময় সঙ্গম রায় বাদশাহি সৈন্যদের রসদদার হলেন। তাঁর কাজে অত্যন্ত খুশি হয়ে বাদশাহ তাঁকে করে দিলেন চারহাজারি মনসবদার। হয়ে উঠলেন বর্ধমান অঞ্চলের একজন ধনী সওদাগর। বৈকুণ্ঠপুরে একটি নদী আছে বলুকা। নদীটি এখন শুকিয়ে গেছে। এই নদীর ধারেই সঙ্গম রায়ের বাসভবন ছিল।
বন্ধুবিহারী রায় : সঙ্গম রায়ের পরলোকগমনের পর পুত্র বন্ধুবিহারী বর্ধমানের ফৌজদারের অধীনে বর্ধমান চাকলার মুনসেফদারি পেলেন। এই রায় বংশ দিল্লির সম্রাটের খুব কাছের মানুষ ছিলেন। বিপদে আপদে তাঁদের প্রচুর সাহায্য করতেন। এরই ফলে তাঁকে দেওয়া হয় রায়রায়ান উপাধি।
আবুরাম রায় : রায়রায়ান বন্ধুবিহারীর মৃত্যুর পর আবুরাম রায় বর্ধমান শহরের রেকাবিবাজার ও মোগল টুলির কোতোয়াল ও চৌধুরীপদ পেলেন জায়গির সহ। তিনি ১৬৫৭ খ্রিস্টাব্দে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বর্ধমানে চলে এলেন। দিল্লির সিংহাসনে তখন সম্রাট শাহজাহান। বর্ধমান রাজবংশের প্রকৃত আদি পুরুষ আবু রায়। বর্ধমান শহরের পশ্চিমদিকে কাঞ্চননগরে বারোদুয়ারি নামে একটি বসতবাটি নির্মাণ করালেন।
বাবুরাম রায় : আবুরাম রায়ের মৃত্যুর পর বাবুরাম রায় হলেন উত্তরাধিকারী। খুব অল্পদিনই জীবিত ছিলেন।
ঘনশ্যাম রায় : বাবুরামের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ঘনশ্যাম বর্ধমানের কোতোয়াল হলেন। এই প্রথম শুরু হল প্রজাদের সেবা। শহরবাসীর জলকষ্ট দূর করার জন্য একটি বিরাট জলাশয় খনন করালেন। যার নাম শ্যামসায়র। এই অঞ্চলটি এখন খুবই উন্নত। পশ্চিমদিকে আধুনিক যুগের সমস্ত সুবিধাযুক্ত মেডিকেল কলেজ, হাসপাতাল, বিজয়চাঁদ দাঁতব্য। চিকিৎসালয়, বর্ধমান রায় কলেজ। সায়রের চারপাশে অতি সুন্দর শান বাঁধানো ঘাট। পূর্বদক্ষিণ কোণে হরিসভা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, বর্ধমান শাখা। ঈশানেশ্বর শিবমন্দির। (জনশ্রুতি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ এই মন্দিরে পূজা করেছিলেন), শ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রম। সায়রের দক্ষিণে হরিসভা গার্লস স্কুল। এইসব জায়গা বর্ধমান রাজ পরিবারের দান।
কৃষ্ণরাম রায় : ঘনশ্যাম রায়ের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র কৃষ্ণরাম রায় ঔরঙ্গজেবের ফরমান অনুসারে ১৬৮৯ সালে বর্ধমানের জমিদারি ও চৌধুরিপদে উত্তরাধিকারী হলেন। তিনি একটি বিশাল দিঘি খনন করালেন। নাম হল কৃষ্ণসায়র। সেইসময় মুদ্রা হিসেবে প্রচলিত ছিল কড়ি। এই বিশাল দিঘিটি খনন করতে প্রচুর কড়ি লেগেছিল। এটি বর্তমানে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পত্তি।
১৬৯৬ সাল। বর্ধমান রাজপরিবারের পক্ষে খুবই খারাপ সময়। ওই সময় চিতুয়া ও বরদার জমিদার শোভা সিংহ আর আফগান সরদার রহিম খাঁ একত্রিত হয়ে ঔরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। মোগলদের প্রিয় ও আশ্রিত কৃষ্ণরাম রায় প্রাণ হারালেন। বর্ধমানের বহু এলাকা বিদ্রোহীদের দখলে চলে গেল।
পূর্বপুরুষদের কুলদেবতা লক্ষ্মীনারায়ণকে বৈকুণ্ঠপুর থেকে এনে বর্ধমানে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন আবু রায়। কৃষ্ণরাম রায় সেই বিগ্রহকে সরিয়ে এনেছিলেন তাঁর প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরে। বিদ্রোহীরা এই কুলদেবতাকেই শুধু নয়, শিবমঙ্গল কাব্যের কবি রামকৃষ্ণ রায়ের গৃহদেবতা রাধাবল্লভকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল। এই রাধাবল্লভকেও একসময় উদ্ধার করেছিলেন কৃষ্ণরাম। এই হামলায় দুটি বিগ্রহই বিধর্মীদের হাতে চলে গেল।
জগৎরাম রায় : ১৬৯৬ সালের জানুয়ারি। কৃষ্ণরাম ওইদিন নিহত হয়েছেন। রাজবাড়ি বিদ্রোহীদের কবলে। পুত্র জগৎরাম গা ঢাকা দিয়ে পালালেন ঢাকায়। শোভা সিংহ রাজপরিবারের মহিলাদের বন্দি করল। তার নজর পড়ল রূপসী রাজকুমারী সত্যবতীর ওপর। এক রাতে শোভা সিংহ রাজকুমারীর সম্ভ্রম নষ্ট করার চেষ্টা করল। বীরাঙ্গনা সত্যবতী তাঁর ঘাগরার মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিলেন একটি ছুরি। সেই অস্ত্র বসিয়ে দিলেন লম্পট শোভা সিংহের বুকে। শোভা সিংহের জীবন এইভাবেই শেষ হল। রইল রহিম খাঁ। সে এইবার। বিদ্রোহ পরিচালনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিল। ওদিকে ওড়িশা, এদিকে হুগলি, মাঝখানে বর্ধমান। চতুর্দিকে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ল। লুঠপাট, নারীদের সম্ভ্রম নষ্ট ইত্যাদি যত অনাচার আছে সবই এত উদগ্র হল যে জনজীবন বিপর্যস্ত। ঔরঙ্গজেব তাঁর পৌত্র আজিম-উশ-শানকে। বিদ্রোহ দমন করার জন্য বাংলার সুবেদার নিযুক্ত করে বর্ধমানে পাঠালেন। ওদিকে ঢাকার নবাবপুত্র জবরদস্ত খান এই বিদ্রোহ দমনে জগৎরামকে নানাভাবে সাহায্য করতে লাগলেন। উভয়ের সমবেত চেষ্টায় বিদ্রোহীরা জব্দ হল। জগঞ্জামের কাজে সন্তুষ্ট হয়ে বাদশাহ তাঁকে ফরমান দিয়ে সম্মান জানালেন। বর্ধমানের উপকণ্ঠে আজিমের কাছে বিদ্রোহীরা সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হল। জগৎরাম শুধু তাঁর জমিদারি ফিরে পেলেন না, তার আয়তনও বেড়ে গেল। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই, ১৭০২ সালে জগৎরাম আততায়ীর হাতে প্রাণ হারালেন। পুত্র কীর্তিচাঁদ উত্তরাধিকারী হলেন। এই রাজবংশে কীর্তিচাঁদ এক উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি। যদিও রাজা উপাধিতে তিনি ভূষিত হননি।
রাজকুমারী সত্যবতী তাঁর সতীত্ব রক্ষার জন্য সুকৌশলে শোভা সিংহকে হত্যা করেছিলেন। সেদিন সত্যবতী ছাড়া রাজপুরীর দশজন সধবা ও তিনজন বিধবা হীরে চিবিয়ে আত্মবিসর্জন দিয়েছিলেন। রাজবাড়ির ইতিহাসে এই দিনটি চিহ্নিত হয়েছে জহুরীতিথি হিসেবে। যাঁরা প্রাণ দিলেন তাঁদের বলা হয় জহুরি। কারণ অমূল্য রত্ন হীরা তাঁদের রক্ষা করেছিল। রাজ ইতিহাসে জহুরিদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। তাঁরা হলেন –১) কুণ্ডুদেবী, ২) হোতা দেবী, ৩) চিমো দেবী, ৪) লক্ষ্মী দেবী, ৫) আনন্দ দেবী, ৬) কিশোরী দেবী, ৭) কুঞ্জ দেবী, ৮) জিতু দেবী, ৯) মূলক দেবী, ১০) দাসো দেবী, ১১) লাজো দেবী, ১২) পাতো দেবী, ১৩) কৃষ্ণা দেবী।
কীর্তিচাঁদ রায় : জগৎরামের দুই ছেলে–কীর্তিচাঁদ আর মিত্র রাম। পিতার মৃত্যুর পর কীর্তিচাঁদ ক্ষমতায় এলেন। নানা কারণে কীর্তিচাঁদ এক অসাধারণ ব্যক্তি। যেমন সুন্দর দেখতে সেইরকম আজানুলম্বিত বাহু। সবাই বলতেন, ইনি শাপভ্রষ্ট অর্জন। এই পরিবারে তিনিই ছিলেন অমিতশক্তিশালী এক যোদ্ধা। তাঁর লেফটেনান্ট কর্নেল ছিলেন–বৎস রাম খান্না। বর্ধমান রাজের সঙ্গে অন্যান্য জেলার যুদ্ধও হত। কীর্তিচাঁদ চন্দ্রকোণা (মেদিনীপুর) এবং বরদা (ঘাটাল) জয় করতে চলেছেন। তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে। পূর্বপুরুষ আবু রায় বর্ধমানের কাঞ্চননগরে রথতলার প্রতিষ্ঠাতা। সেই জায়গায় এক সাধু দিনরাত ধুনি জ্বালিয়ে বসে থাকতেন। তিনি কীর্তিচাঁদের যুদ্ধযাত্রা দেখে বলে উঠলেন, মহারাজের জয় হোক। কীর্তিচাঁদ থমকে দাঁড়ালেন। সাধুজিকে বললেন, আমি যতদিন না ফিরি ততদিন আপনি এখানেই থাকবেন। রাজকর্মচারীদের বলে পাঠালেন, মাথার ওপর সুন্দর একটি আচ্ছাদন তৈরি করে দাও আর রাজপ্রাসাদ থেকে প্রতিদিন যেন সেবা আসে।
যুদ্ধজয় করে কীর্তিচাঁদ ফিরে এলেন। সন্ন্যাসীকে পাঁচশো বিঘা নিষ্কর সম্পত্তি দান করলেন। তৈরি করে দিলেন বিশাল একটি মন্দির ও প্রাসাদ। পরবর্তীকালে এই সাধুই রাজগঞ্জের নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের আদি পুরুষ বলে সর্বত্র পরিচিতি পেলেন। কীর্তিচাঁদ অনেক ছোট ছোট রাজ্য জয় করে তাঁর নামের সার্থকতা প্রতিপন্ন করেন। চন্দ্রকোণা জয় করার পর রথযাত্রার দিন প্রকাশিত হয় কীর্তিচাঁদ রথ। প্রচুর ধূমধাম। সপ্তাহব্যাপী মেলা, কীর্তিচাঁদ রথে তাঁর বিজয় ঘোষণা। এই উৎসব স্থায়ী হল কাল থেকে কালান্তরে। তাঁর জয়গানে কবিরা মুখর হলেন, যদিও তিনি রাজা বা মহারাজা উপাধি পাননি, কিন্তু সেই সাধু তাঁকে মহারাজ বলেই সম্বোধন করেছিলেন। তাঁর সময়ে জমিদারির সীমা প্রসারিত হয়েছিল। বিষ্ণুপুরের রাজারা তাঁর কাছে পরাজিত হয়েছিলেন। চন্দ্রকোণার রাজা মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে শোভা সিংহের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন। কীর্তিচাঁদ তাঁকেও শেষ করলেন।
চিত্রসেন রায় : কীর্তিচাঁদের পুত্র চিত্রসেন। তিনিই প্রথম রাজ উপাধি লাভ করেন। সাল ১৭৪১। তখন মোগল সম্রাট ছিলেন মহম্মদ শাহ। সম্রাটের অনুমতি নিয়ে আরও কয়েকটি পরগনা তিনি দখল করেছিলেন। চিত্রসেনের সময় মণ্ডলঘাট, আরসা, চন্দ্রকোণার পুরোটা বর্ধমানের অধিকারভুক্ত হয়। যুদ্ধ করে বীরভূম, পঞ্চকোট ও বিষ্ণুপুরের অনেকটা তিনি দখল করে নেন। রাজগড়ে নির্মাণ করলেন প্রথম দুর্গ। দ্বিতীয় দুর্গ হল বীরভূমের প্রান্তে অজয়নদের তীরে–সেন পাহাড়ি। এই সময় বাংলায় ঘনিয়ে এসেছিল প্রবল দুর্দিন। একটি হল বর্গির হাঙ্গামা অপরটি ছিয়াত্তরের মন্বন্তর। মহারাষ্ট্রের একদল নিষ্ঠুর লুঠেরা বাংলাদেশটাকে প্রায় শ্মশান করে দিয়েছিল। সাল ১৭৪৯। গ্রাম এবং শহর লুঠ করে, খুন করে, যে কোনও বাড়িতে ঢুকে যথাসর্বস্ব হরণ করে, ধানের গোলায় আগুন লাগিয়ে–এই বর্গিরা রঘুজি ভোঁসলের নেতৃত্বে তাণ্ডব শুরু করে দিয়েছিল। ভাবতে অবাক লাগে তাদের সঙ্গে ছিল প্রায় চল্লিশ হাজার অশ্বারোহী ফৌজ। ওড়িশা দিয়ে ঢুকে ছড়িয়ে পড়ত পঞ্চকোট, বিষ্ণুপুর, বীরভূম, মেদিনীপুর ও বর্ধমানে। এই সমগ্র এলাকাটা ছিল বারবার আক্রমণের লক্ষ্যস্থল। বর্ধমান জেলার কাটোয়া পর্যন্ত একটা জায়গাও তাদের আক্রমণের বাইরে রইল না। জমির সমস্ত ফসলই শুধু নষ্ট করল না উর্বরতাও শেষ করে দিল। বর্ধমানের শস্য ভান্ডার শেষ। বাইরে থেকে আনার পথও বন্ধ। অনাহারে প্রাণ যায়। মানুষ গাছের পাতা ও শেকড় খেতে শুরু করল। তাও একদিন শেষ হয়ে গেল। বর্গির হামলার যদি একটি মানচিত্র আঁকা যায় তাহলে দেখা যাবে–ওদিকে রাজমহল, এদিকে মেদিনীপুর ও জলেশ্বর পর্যন্ত সুবিস্তৃত একটি অঞ্চল বর্গির আক্রমণে প্রায় ধ্বংস। তাঁদের নিষ্ঠুরতার কোনও তুলনা ছিল না। মানুষের নাক, কান কাটছে, এমনকী হাত দুটোও উড়িয়ে দিচ্ছে। সমস্ত মৃতদেহ ফেলা হচ্ছে নদীর জলে। এক-একটি হত্যাকাণ্ডের এক-এক পদ্ধতি। কারও গলায় ময়লা ভর্তি বস্তা বেঁধে, হাত-পা কেটে জলে ফেলে দিল। কারওকে জীবন্ত পুড়িয়ে ছাই করে দিল। গঙ্গারামের মহারাষ্ট্র পুরাণে প্রত্যক্ষ একটি বর্ণনা আছে।
তবে সব বরগি গ্রাম লুটতে লাগিল
যত গ্রামের লোক সব পলাইল।
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পলায় পুঁথির ভার লইয়া
সোনার বাহনা পলায় সোনার ভার লইয়া।
গন্ধবণিক পলায় দোকান লইয়া যত
তামা পিতল লইয়া কাঁসারি পলায় কত।
শঙ্খ বণিক পলায় করাত লইয়া যত।
চতুর্দিকে লোক পলায় কি বলিব কত।
নবাব আলিবর্দির চেষ্টায় বর্গিরা কিছুটা পিছু হটলেও নবাবকে কাটোয়া দুর্গে আশ্রয় নিতে হল। ১৭৪২ সালে কাটোয়ায় দু-পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ হল। ভাস্কর পণ্ডিত পরাজিত হয়ে পঞ্চকোটের দিকে পালিয়ে গেল। কিছু পরে শক্তিসঞ্চয় করে চন্দ্রকোণার ভেতর দিয়ে। মেদিনীপুরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। অবশেষে আলিবর্দি তাদের সঙ্গে সন্ধি করলেন। সন্ধির চুক্তি অনুসারে কটকশহরটি ছেড়ে দিতে হল। আর বছরে বারো লাখ টাকা চৌথ হিসাবে। মারাঠাদের অর্থকোষে জমা দেওয়ার শর্ত মেনে নিতে বাধ্য হলেন নবাব। সেইসময় ছেলেদের ঘুম পাড়াবার সময় মায়েরা ঘরে ঘরে সুর করে বলতেন–
ছেলে ঘুমাল পাড়া জুড়াল
বর্গি এল দেশে
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে
খাজনা দেব কিসে।
এই ডামাডোলের সময়েই মহারাজ তিলকচাঁদ মূলাজোড়ের কাছে কাউগাছিতে রাজধানী সরিয়ে এনেছিলেন। সে কথা পূর্বেই বলা হয়েছে।
এইখানেই সেই ঘটনাটি মূল কাহিনির সঙ্গে জোড়া লাগল।
রাজা চিত্রসেনের কোনও সন্তানাদি ছিল না। তিনি পরলোকগমন করার পর বর্ধমান রাজপরিবার ভিন্ন শাখায় চলে গেল। তাঁর পিতৃব্যপুত্র তিলকচাঁদ ক্ষমতায় এলেন। তাঁর ভাগ্য অতি প্রসন্ন। মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম ১৭৬৪ সালে তাঁকে রাজবাহাদুর করে চার হাজার পদাতিক ও দু-হাজার অশ্বারোহী রাখার অনুমতি দিলেন। চার বছর পরেই ১৭৬৮ সালে তিনি হলেন মহারাজাধিরাজ, হয়ে গেলেন পাঁচ হাজারি মনসবদার। তাঁর বাহিনীতে আরও তিন হাজার অশ্বারোহী যুক্ত হল। কামান ও বন্দুকের শক্তিও পেলেন। সেই সময় বাংলায় ইংরেজ শক্তি প্রবল হচ্ছে। তখন বড় পিচ্ছিল অবস্থা। ১৭৬০ সালে তিলকচাঁদ ও বীরভূমের রাজা আসাদউল্লাহ একত্রিত হয়ে ক্যাপ্টেন হোয়াইটকে পরাজিত করলেন। এই বছরটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১৭৫৬ সালে আলিবর্দি চলে গেলেন পরলোকে। আর তার এক বছরের মধ্যেই পলাশি। বাংলা পরাধীন হল। মিরজাফর নামেমাত্র নবাব। প্রকৃত প্রভু ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। অতি সমৃদ্ধ বর্ধমান কোম্পানির দখলে চলে গেল। কিন্তু তাঁরা তিলকচাঁদকে বন্ধু হিসাবেই গ্রহণ করলেন। একসময় মীরজাফরকেও যেতে হল। ১৭৬০ সালে মীরকাশেমকে বসানো হল মসনদে। তিনি বর্ধমানের রাজস্ব ধার্য করলেন। ৩১,৭৫,৪০৬ সিক্কা। এই কর দেওয়ার সংগতি মহারাজ তিলকচাঁদের ছিল না। মারাঠারা সব শেষ করে দিয়ে গেছে। মহারাজা উঁকিলের মাধ্যমে রাজ্যের অবস্থা কোম্পানিকে জানালেন। বর্গির হাঙ্গামায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় আট লাখ টাকা। রাজস্ব কিছুই আদায় হয়নি। কোম্পানি একটি সমঝোতায় এলেন। রাজস্বের পরিমাণ দাঁড়াল এগারো লক্ষ টাকা। কিস্তিতে কিস্তিতে দিতে হবে। তিলকচাঁদের পক্ষে দায়পরিশোধ করা সম্ভবপর হয়নি। ঠিক সেই সময় বীরভূম আর মেদিনীপুরে কোম্পানি বিরুদ্ধে সেখানকার রাজারা বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। তখন ইংরেজ কোম্পানি কোনও উপায় না দেখে বর্ধমানের মহারাজাকে মিত্র হিসেবেই গণ্য করলেন। রাজস্ব আদায় করার জন্য ১৭৬১ সালে বর্ধমানে একজন রেসিডেন্ট নিযুক্ত করলেন। এতেও কোনও সুরাহা হল না। রাজস্ব বাবদ প্রায় ছাব্বিশ লক্ষ টাকা বকেয়াই রয়ে গেল। তখন বর্ধমান মহারাজার কিছু কিছু জমিদারি হাতছাড়া হয়ে গেল। এর ফলে হুগলি ও বর্ধমানে নতুন একদল জমিদারের আবির্ভাব হল।
মারাঠা আক্রমণে কাটোয়া সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। গ্রামাঞ্চলে কেউ ছিল না বললেই চলে। গ্রাম ছেড়ে মানুষ পালিয়েছিল বনে বাদাড়ে, জলায় (ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ারে সেই খবর আছে)। মহারাজা তিলকচাঁদের সময় যথেষ্ট উদ্বেগপূর্ণ। তাঁর দুই বিবাহ। প্রথম স্ত্রীর নাম বিষণকুমারী দেবী। তাঁরই পুত্র মহারাজ তেজচাঁদ বাহাদুর। দুই কন্যা–তোতাকুমারী ও চিত্রকুমারী। বর্ধমান শহরের বিখ্যাত রানিসায়র সরোবরটি বিষণকুমারী দেবীর কীর্তি। দ্বিতীয় স্ত্রীর নাম রূপকুমারী দেবী। তিনি নিঃসন্তান। এ ব্যাপারে সামান্য মতভেদ আছে। কারও মতে রূপকুমারীই প্রথম স্ত্রী। মহারাজ তিলকচাঁদ রেকাবি বাজার এলাকায় বর্তমান রাজপ্রাসাদ তৈরির কাজ শুরু করান। তাঁরই সময়ে শ্রী শ্রী লক্ষ্মীনারায়ণ জিউ ও ভুবনেশ্বর মহাদেবের মন্দির দুটিও নির্মিত হয়। রাজপ্রাসাদ অসম্পূর্ণ রেখেই তিনি দেহত্যাগ করেন ১৭৭১ সালে। এই সময়েই সেই ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। রাজকোষ শূন্য। রাজবাড়ির জিনিসপত্রও বিক্রি করতে হয়েছে। পারলৌকিক ক্রিয়ার অর্থ চাইতে হয়েছে ইংরেজ সরকারের কাছে। এরপরে। ক্ষমতায় এলেন তেজচাঁদ। বর্ধমানের এক বর্ণময় চরিত্র।
তেজচাঁদ যখন ক্ষমতায় বসলেন তখন তিনি নাবালক। তাঁর মা বিষণকুমারী দিল্লির বাদশাহ শাহ আলমের ফরমান নিয়ে রাজকার্য চালাতে লাগলেন। তাঁর অপূর্ব দক্ষতায় রাজভান্ডার। আবার ভরে উঠল। তাঁর খরচের বহর দেখলেই বোঝা যেত সুদিন ফিরেছে। সেইকালে এক লক্ষ টাকারও বেশি খরচ করে নবাব হাটে একশোনটি শিবমন্দির তিনি প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠার দিন সারা ভারতের বিভিন্ন এলাকা থেকে এক লক্ষেরও বেশিব্রাহ্মণ পণ্ডিত এসেছিলেন। মহারাজা তেজচাঁদ নিজে ব্রাহ্মণদের পদপ্রক্ষালন ও পদরজ সংগ্রহ করেন। অবশ্যই ঐতিহাসিক কীর্তি। এই মন্দির সমন্বয় বর্ধমানের পশ্চিমদিকে জিটি রোড ও সিউড়ি রোডের সংযোগস্থলে অবস্থিত। আজও হাজার হাজার মানুষ শিবরাত্রির দিন সেখানে সমবেত হন। পরবর্তীকালে বিড়লা স্ট্রাস্ট এটির সংস্কার করেন। ১৭৭৯ সালে তেজচাঁদ সাবালক হলেন। ১৭৯৩ সালে ইংরেজ সরকার একটি আইন প্রণয়ন করলেন–Regulation one, মহারাজের সঙ্গে ইংরেজ সরকারের চুক্তি হল। রাজস্ব ধার্য হল, ৪০,১৫,১০৯ সিক্কা। আর পুলবন্দি বাবদ ১,৯৩,৭২১ সিক্কা। আবার সেই এক ব্যাপার, দুর্ভিক্ষের জন্য মহারাজার পক্ষে রাজস্বের পুরো টাকা মেটানো সম্ভব হল না। জমিদারির কিছু অংশ বিক্রি হয়ে গেল। কিনলেন সিঙ্গুরের দ্বারিকনাথ সিংহ, ভাসতারার ছকু সিংহ, জনাইয়ের বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ। অবশেষে পত্তনি প্রথা চালু করে তেজচাঁদ জমিদারি রক্ষা করলেন।
অনেক ভালো কাজ তিনি করেছেন। ১৮১৭ সালে বর্ধমানে একটি অ্যাংলো ভার্নাকুলার স্কুল স্থাপন করেন। পরে মহতাব চাঁদ এটিকে হাইস্কুল এবং ১৮৮১ সালে এটিকেই উন্নিত করলেন আই.এ.কলেজে।
তেজচাঁদের অন্য জীবন। তিনি বিলাসী এবং ভোগী। একবার নয়, আটবার বিবাহ করেছিলেন। প্রখ্যাত লেখক সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখছেন–শিরোনাম, তেজচাঁদ বাহাদুর (বর্ধমানের বুড়া রাজা)–প্রতিদিন প্রাতে দেওয়ান, মোসাহেব ও অন্যান্য কর্মচারীরা। অন্দরমহলের দ্বারে আসিয়া তেজচাঁদ বাহাদুরের বহির্গমন প্রতীক্ষা করিতেন; তিনি যথাসময়ে এক স্বর্ণপিঞ্জর হস্তে বহির্গত হইতেন, পিঞ্জরে কতকগুলি লাল নামা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পক্ষী আবদ্ধ। থাকিত, তিনি তাহাদের ক্রীড়া ও কোন্দল দেখিতে দেখিতে আসিতেন। সমুখবর্তী হইবা মাত্র তাঁহাকে সকলে অভিবাদন করিত, মহারাজা হাসিমুখে তাহাদের আশীর্বাদ করিতেন। একদিন প্রাতে তিনি পিঞ্জর হস্তে অন্দরমহল হইতে বহির্গত হইতেছেন, এমন সময় একজন প্রধান কর্মচারী অগ্রসর হইয়া করজোড়ে নিবেদন করিল মহারাজ, হুগলিতে খাজনা দাখিল করিবার নিমিত্ত সে দিবস যে এক লক্ষ টাকা পাঠানো হইয়াছিল, তাহা তথাকার মোক্তার। আত্মসাৎ করিয়া পলাইয়াছে। তেজচাঁদ বিরক্ত হয়ে উত্তর করিলেন, চুপ! হামরা লাল ঘবরাওয়েগা! এক লক্ষ টাকা গেল শুনিয়া তাঁহার কষ্ট হইল না, কিন্তু কথার শব্দে লালপক্ষী। ভয় পাইবে, এই জন্য তাঁহার কষ্ট হইল। এই মনে করিয়া কর্মচারী বড় রাগ করিলেন, পাপিষ্ঠ মোক্তারকে সমুদয় টাকা উদগীরণ করাইব, নতুবা কর্মত্যাগ করিব এই সঙ্কল্প করিলেন। মোক্তারের অনুসন্ধান আরম্ভ হইল। কিছুকাল পরে সংবাদ আসিল যে, মোক্তার আপন বাটিতে বসিয়া পুষ্করিণী কাটাইতেছে, দেউল দিতেছে, আর যাহা মনে আসিতেছে তাহাই করিতেছে। তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য রাজ্যসরকার হইতে সিপাহি ও হাওয়ালদার বাহির হইল। কিন্তু রাজা তেজচাঁদ প্রথমে তাহা জানিতেন না; কিছুদিন পরে তাহা শুনিয়াছিলেন। মোক্তার ধৃত হইয়া রাজবাটীতে আনীত হইলে তেজচাঁদ বাহাদুর মোক্তারকে জিজ্ঞাসা করিলেন :
তুমি আমার এক লক্ষ টাকা চুরি করিয়াছ?
মোক্তার–না, মহারাজ, আমি চুরি করি নাই, আমি তাহা বাটীতে লইয়া গিয়াছি।
তেজচন্দ্র–কেন লইয়া গেলে?
মোক্তার–মহারাজের কার্যে ব্যয় করিব বলিয়া লইয়া গিয়াছি। আমাদের গ্রামে একটিও শিবমন্দির ছিল না, কুমারীরা শিবমন্দিরে দীপ দানের ফল পাইত না, যুবতীরা শিবপূজা করিতে পাইত না। এক্ষণে মহারাজের পুণ্যে তাহা পাইতেছে। আর, একটি অতিথিশালা করিয়াছি, ক্ষুধার্ত পথিকেরা এখন অন্ন পাইতেছে।
তেজচন্দ্র–তুমি কি সমুদয় টাকা ইহাতেই ব্যয় করিয়াছ?
মোক্তার–আজ্ঞা না মহারাজা আমাদের দেশে বড় জলকষ্ট ছিল, গোবৎসাদি দুই প্রহরের সময় একটু জল পাইত না, আমি মহারাজের টাকায় একটি বড় পুষ্করিণী কাটাইয়াছি। মহারাজের পুণ্যে তাহার জল কীরূপ আশ্চর্য পরিষ্কার ও সুস্বাদু হইয়াছে, তাহা সিপাহিদের জিজ্ঞাসা করুন।
তেজচন্দ্র–পুষ্করিণীটি প্রতিষ্ঠা করিয়াছ?
মোক্তার–আজ্ঞা না! টাকায় কুলায় নাই।
তেজচন্দ্র–এখন কত টাকা হইলে প্রতিষ্ঠা হয়?
মোক্তার–ন্যূনকল্পে আর দুই হাজার চাই।
তেজচন্দ্র–কিন্তু দেখো! খবরদার!–দুই হাজার টাকার এক পয়সা বেশি না লাগে, তাহা হইলে আর আমি দিব না।
তাহার পর পূর্বকথিত কর্মচারীকে ডাকিয়া মহারাজ বলিলেন, আমি তো মোক্তারের কোনও দোষ দেখিতে পাইলাম না। মোক্তার যাহা করিয়াছে, তাহাতে আমার টাকা সার্থক হইয়াছে। ইহা অপেক্ষা আমি আর কি ভালো ব্যয় করিতাম। কর্মচারী নিরুত্তর হইল।
তেজচাঁদ বাহাদুরের বিবাহ কাণ্ডে আসার আগে তাঁর চরিত্রের কয়েকটি বিশেষ দিকে আলোকপাত করা যেতে পারে। বৃদ্ধ বয়সে তাঁকে দেখে সঞ্জীবচন্দ্র যেসব মন্তব্য করেছেন। তার আড়ালে আর একটি মহৎ জীবন খুঁজে পাওয়া যায়। যৌবনে তিনি একজন উচ্চাঙ্গের সাধক ছিলেন। সম্ভবত তন্ত্র। পরমশ্যামা সাধক কমলাকান্তের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে। বর্ধমানের বোরহাট অঞ্চলে কমলাকান্ত তাঁর আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। বহুপ্রচলিত একটি লোককাহিনি আছে কমলাকান্ত মহারাজাধিরাজ তেজচাঁদকে অমাবস্যার রাতে পূর্ণিমার চাঁদ দেখিয়েছিলেন, আর সুরাকে রূপান্তরিত করেছিলেন দুগ্ধে। তেজচাঁদ বাহাদুরের আমলেই বর্ধমান শহরে রাধাবল্লভ জিউ ও অন্নপূর্ণাদেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। কলকাতার পেনোপোস্তা, ওল্ডচিনাবাজার, টেরেটো বাজার শ্রীশ্রী রাধাবল্লভজিউর সেবায় দান করেন। বর্ধমান রাজপ্রাসাদটিও তিনি সম্পূর্ণ করান। শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ ঠাকুরের আবির্ভাব চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্য মস্ত বড় একটি কাজ করেছিলেন। বাঁকা নদীর দক্ষিণ দিকে সাধারণের যাতায়াতের সুবিধার জন্য যে ভাঙা পুলটি ছিল সেটিকে সম্পূর্ণ সংস্কার করে একটি পাকা পুল নির্মাণ করান। এই পুলটি এখন আলমগঞ্জের পুল নামে পরিচিত। একটি শ্বেতপাথরের ফলকে উৎকীর্ণ আছে, ঈশ্বর রাধাবল্লভ ঠাকুরের আবির্ভাব জন্য সুখেতে প্রকাশ ইত্যাদি। তাঁর এইসব কাজে যিনি সর্বদা পাশে থেকেছেন তিনি হলেন মহিষী কমলকুমারী। তেজচাঁদের ষষ্ঠপত্নী এই কমলকুমারী।
প্রথম পত্নী জয়কুমারী দেবী। জাজপুরের মেয়ে। পিতার নাম অজ্ঞাত। দ্বিতীয় মহারানি প্রেমকুমারী। তাঁর আর একটি নাম পেয়ারকুমারী। উখরার উড়রমল শেঠের কন্যা। তৃতীয়, মহারানি সেতাবকুমারী। পিত্রালয় ফতেপুরে। লালা বাহাদুর সিংহের ভগিনী কন্যা, চতুর্থ মহারানি তেজকুমারী দেবী, পঞ্চম, মহারানি নানকীকুমারী দেবী, পিতার নাম পাঞ্জাব রায় ট্যান্ডন। তাঁরই গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন প্রতাপচাঁদ। যাঁকে নিয়ে তোলপাড় ইতিহাস। সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অনুসন্ধানমূলক গ্রন্থ জাল প্রতাপচাঁদ। ষষ্ঠ পত্নী, মহারানি কমলকুমারী দেবী। তাঁর বিবাহ বিশেষ উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। মহারাজা তেজচাঁদ তখন মধ্যবয়সি। সঞ্জীবচন্দ্রের বিশেষণে বর্ধমানের বুড়ো রাজা। তিনি জাল প্রতাপচাঁদ-এ লিখছেন, মহারাজ একদিন একটি দরিদ্র বালিকাকে পথে খেলিতে দেখিলেন, বালিকা পরমা সুন্দরী। মহারাজ তৎক্ষণাৎ তাহার পিতার সন্ধানে লোক পাঠাইলেন। তোক আসিয়া বলিল। পিতার নাম কাশীনাথ, জগন্নাথ দর্শনে যাইবে বলিয়া সপরিবারে লাহোর হইতে এখানে আসিয়াছে। জাতিতে ক্ষত্রিয়। মহারাজের আর বিলম্ব সইল না, দরিদ্রকে অর্থলোভ দেখাইয়া কন্যাটিকে বিবাহ করিলেন। তিনিই মহারানী কমলকুমারী। রাজবাড়ির তথ্য একটু অন্যরকম–সঞ্জীবচন্দ্রের বর্ণনায় আছে দরিদ্রের কন্যা রাস্তার খেলা করছিলেন, আসল ঘটনা খেমচাঁদ কাপুর তাঁর ছেলে ও মেয়েকে নিয়ে পুরীতে জগন্নাথ দেবকে দর্শন করতে যাচ্ছিলেন। কেশবগঞ্জের চটিতে তাঁরা যখন বিশ্রাম করছিলেন সেই সময়ে তেজচাঁদ বাহাদুর কোথাও যাচ্ছিলেন। হঠাৎ মেয়েটির ওপর তাঁর দৃষ্টি পড়ল। তিনি এতটাই উতলা হলেন যে, তাঁর বাবাকে প্রচুর অর্থে সন্তুষ্ট করে মেয়েটিকে বিবাহ করলেন। পুরো পরিবারটি বর্ধমানে আশ্রয় পেল। এই কমলকুমারীর ভাই পরাণচাঁদ, তিনি এইবার বেশ জাঁকিয়ে বসলেন। হয়ে গেলেন দেওয়ান। সঞ্জীবচন্দ্রের লেখায়, প্রায়ই উল্লেখ পাওয়া যাবে কুচুটে, ষড়যন্ত্রকারী পরাণবাবুর। তেজচন্দ্রকে অতিষ্ঠ করে তোলার মতো একটি চরিত্র। তাঁরই উৎপাতে মহারাজার একমাত্র পুত্র প্রতাপচাঁদ কোথায় হারিয়ে গেলেন। কাটোয়ার গঙ্গার তীরে তাঁর অন্তর্জলি হল। তাঁকে দাহ করাও হল। কিন্তু সতেরো বছর পরে তিনি আবার ফিরে এলেন। শুরু হল মামলা। সঞ্জীবচন্দ্রের বইয়ের উপাদান–জাল প্রতাপচাঁদ।
পরাণচাঁদ কাপুর এইবার বর্ধমানের রাজগৃহে তাঁর জাল বিস্তার করলেন। তেজচাঁদের তখনও নিবৃত্তি আসেনি। কমলকুমারীকে বিয়ের পরেই ঘনশ্যাম চাঢ্যের কন্যা উজ্জ্বলকুমারীকে বিবাহ করলেন। পত্নীর সংখ্যা দাঁড়াল সাত। এরপর দেওয়ান পরাণচাঁদ ফেললেন পাশার শেষ দান। তাঁর বালিকা কন্যাটিকে নিবেদন করলেন তেজচাঁদের পত্নীকুলে। তিনি হলেন অষ্টম ও শেষ মহারানি। নাম বসন্তকুমারী। তিনি তখন চলিত বাংলায় বলতে গেলে কচি খুকি, পিতা পরাণচাঁদের দুষ্ট অভিসন্ধি পূরণের জন্য তিনি বলিপ্রদত্ত হলেন। কী কাণ্ড! পরাণচাঁদ তেজচাঁদের শ্যালক এবং শ্বশুর ও দেওয়ান।
জেনানা মহলে বসন্তকুমারীর কী অবস্থা তা পরে জানা যাবে। তিনি যথাসময়ে প্রকাশিত হবেন তাঁর ফণা বিস্তার করে। এত বিয়ে কিন্তু ছেলে একটি। সবেধন নীলমণি প্রতাপচাঁদ। পঞ্চম পত্নী নানকিকুমারী তাঁর মা। ষষ্ঠ রানি কমলকুমারী তাঁর ভ্রাতুস্পুত্র চুনীলালকে দত্তক নিয়েছিলেন। এই চুনীলাল পরাণচাঁদের পুত্র। সে তার মায়ের অষ্টম গর্ভের সন্তান। দেওয়ান পরাণচাঁদের ধারণা অষ্টম গর্ভের সন্তানদের ভাগ্য রাজভাগ্য। প্রতাপচাঁদকে হটাতে পারলেই চুনীলালের বিরাট ভবিষ্যৎ। অন্যমতে চুনীলাল নয় ছেলেটির নাম কুঞ্জবিহারী। তেজচাঁদ অনেক ভালো ভালো কাজ করেছিলেন। কিন্তু পিতা হিসেবে প্রতাপচাঁদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক তেমন ভালো ছিল না। কুমার প্রতাপচাঁদ একজন উদ্ধৃঙ্খল যুবক হয়ে দাঁড়ালেন। সাঁতারে পটু, সুদক্ষ ঘোড়সওয়ার, ক্ষুরধার বুদ্ধি, অল্প বয়সেই তাঁর মাতৃবিয়োগ হয়। পিতামহী মহারানি বিষণকুমারীই তাঁকে মানুষ করেন। তাঁর অতিশয় আদরে প্রতাপচাঁদ এক বেপরোয়া যুবক। কোনও ভয়ডর নেই। তেজচাঁদ বাহাদুর তাঁকে এড়িয়ে চলতেন। সুরা এবং সাকি–দুটিই তাঁর অতি প্রিয়। পরে সাধক কমলাকান্তের সংস্পর্শে এসে একেবারে অন্যরকম। হয়ে গেলেন। কুস্তিগীর, লম্বা চওড়া শরীর, তিরন্দাজিতে ওস্তাদ, লেখাপড়াও করতেন। ১৮১৯ সালের বিখ্যাত অষ্টম বঙ্গ আইনের খসড়া তাঁরই তৈরি। প্রতাপচাঁদেরও দুই বিয়ে। প্রথম স্ত্রীর নাম আনন্দী দেবী, দ্বিতীয় স্ত্রীর নাম পেয়ারিদেয়ী দেবী।
প্রতাপচাঁদ পরাণবাবুকে একেবারেই সহ্য করতে পারতেন না। তেজচাঁদের বসন্তকুমারীর। সঙ্গে বিয়ে কেউই ভালো চোখে দেখেননি, সাধারণ মানুষ বলতে লাগলেন, পরাণমামা দড়ি পাকাচ্ছেন। প্রতাপচাঁদ উঠতে বসতে খালি শুনছেন, সিংহাসনে প্রতাপচাঁদ কী করে বসেন। একবার দেখি। বসবে অষ্টম গর্ভের ওই সন্তানটি। তিনিও বলতে শুরু করলেন, তোমরা লিখে রাখো–আমার গদিতে বসবে পরাণের ছেলে। এরফলে পরাণবাবুরই সুবিধে হল।
তাঁর ষড়যন্ত্রের শেকড় আরও গভীরে চলে গেল। বসন্তকুমারীর সঙ্গে তেজচাঁদের বিয়ের আগে থেকেই দুজনের সম্পর্ক তিক্ত হতে শুরু করেছিল। বসন্তকুমারীকে ভেট দেওয়ার পর থেকে সাপে নেউলে সম্পর্ক হয়ে দাঁড়াল।
প্রতাপচাঁদ নিজের ভাবমূর্তি বদলাবার জন্য রাজকার্যে মন দিয়েছিলেন। সেই সময়ে। জমিদারি রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াত যদি না প্রতাপচাঁদ তাঁর আট আইনটি সরকারকে দিয়ে বলবৎ করাতেন। বর্ধমান রাজাদের বিরাট জমিদারি। যথাসময়ে খাজনা জমা দেওয়া এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। অতি কুখ্যাত সূর্যাস্ত আইনে জমিদারদের জমিদারি কখন যায়, কখন থাকে তার নিশ্চয়তা ছিল না। অধিকাংশ জমিদারের পরমায়ু চার বছরের বেশি হত না। প্রতাপচাঁদের মাথা থেকেই বেরোল, সরকারি খাজনা আদায় না করে জমিদারি ভাগ ভাগ করে এক-একজন জমিদারকে পত্তনি দেবেন। সূর্যাস্ত আইনের মতোই চুক্তি। ঠিক সময়ে খাজনা দিতে না পারলে সেই পত্তনি অন্য জমিদারকে নিলাম করা হবে। আর সেই টাকা থেকে মিটবে সরকারের খাজনা। এরফলে বর্ধমান রাজের জমিদারি শুধু পাকা হল না আয়ত্ত বেড়ে গেল অনেক গুণ।
একদিকে এই কৃতিত্ব অন্যদিকে প্রতাপচাঁদের উচ্ছঙ্খল স্বভাব। তেজচাঁদের কানে পরাণবাবুর ফুসমন্তর। অন্তিম সময়ে দেখা গেল পিতা-পুত্রের বাক্যালাপ পর্যন্ত বন্ধ। আট আইনের প্রণেতা প্রতাপচাঁদকে সবাই দেখলেন। এইবার প্রতাপচাঁদের আর একটি রূপ– ইংরেজ সিভিল সার্ভেন্ট দেখলেই বেধড়ক পেটান। তিনি একজন ঐতিহাসিকের লেখায় পড়েছিলেন, পলাশির যুদ্ধে মিরজাফর হঠাৎ যুদ্ধ থামিয়ে না দিলে ইংরেজদের বাহাদুরি বেরিয়ে যেত। সেই রাগে বলশালী প্রতাপচাঁদ ইংরেজ রাজকর্মচারী দেখলেই পেটাতেন। একবার পথে তাঁর সঙ্গে একজন ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটের দেখা হয়েছিল। তিনি রাস্তার মাঝখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। প্রতাপচাঁদের গাড়ি দেখে তিনি রাস্তা ছাড়েননি। প্রতাপচাঁদ সঙ্গে সঙ্গে সাহেবকে রাস্তায় নামিয়ে আগাপাশতলা বেত দিয়ে পিটিয়েছিলেন। এই অপরাধের জন্য প্রতাপচাঁদের নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা বের হয়েছিল।
ইংরেজ রাজকর্মচারীদের পেটালেও সাহেবদের সঙ্গে তাঁর প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। একসঙ্গে বসে মদ্যপান করতেন। মেদেয়িরা মদটি তাঁর ভীষণ প্রিয়। ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত না হলেও চোস্ত ইংরেজি বলতেন। এক ইংরেজ ডাক্তার স্কটের সঙ্গে তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা ছিল। রাজার ছেলে হলেও অত্যন্ত মিশুকে ছিলেন। দেশি-বিদেশি সকলের সঙ্গেই গড়ে উঠত আত্মীয়তা। তাঁর কতকগুলি আড্ডার স্থল ছিল। যেমন সালকিয়া, তেলেনিপাড়ার রামধনবাবুর বাড়ি। এই জায়গাটি ছিল ভদ্রেশ্বরে। রামধনের বৈঠকখানায় মজলিশ বসত। চুঁচড়োর রাজবাড়িতেও যেতেন। দিনেমারের গভর্নর বারবেক সাহেবের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। এইখানেই আর-একজন ছিলেন হাজি আবু তালিব। সিঙ্গুরের নবাববাবুর সঙ্গে তাঁর ভীষণ খাতির। মুসলমান হলেও নবাববাবু প্রতি বছর দোলের দিন বর্ধমানের ফাগ খেলতে আসতেন। একবার এত ফাগ নিয়ে গিয়েছিলেন, পনেরো দিনেও শেষ করা যায়নি। শেষে বস্তা বস্তা ফাগ বাঁকা নদীর জলে ফেলে দিলেন। নদীর জল টকটকে লাল। স্থানীয় মানুষ কয়েকদিন সেই জল ব্যবহার করতে পারেননি। নবাবের এই নবাবির পরিণাম–তাঁর স্ত্রী বৃন্দাবনে ভিক্ষে করে শেষ জীবন কাটিয়েছিলেন।
প্রতাপচাঁদ যখন বিষয়কর্মে মন দিলেন তখন পরাণবাবু কায়দা করে তাঁকে সেই কাজ থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করতেন। প্রতাপচাঁদ বুঝেছিলেন, এই পরাণমামা কী চাইছেন! তিনি কৌশলে তাঁর পিতার কাছ থেকে সমস্ত বিষয়ের দানপত্র লিখিয়ে নিয়েছিলেন। পরাণবাবু খুব চেষ্টা করেছিলেন সেটিকে খারিজ করাতে। কিন্তু তিনি কিছুই করতে পারলেন না। আর তখনই তাঁর পরমাসুন্দরী কন্যা বসন্তকুমারীকে রাজার ভোগে পাঠিয়ে দিলেন।
হঠাৎ প্রতাপচাঁদের ভীষণ পরিবর্তন এল। ইতিমধ্যে তিনি সাধক কমলাকান্তের সঙ্গলাভ করেছেন। মানসিক পরিবর্তন আসা স্বাভাবিক। ধীরে ধীরে তিনি নিজেকে গুটিয়ে আনছেন। হঠাৎ একদিন তিনি রাজবাড়ি থেকে অদৃশ্য হলেন। তেজচাঁদ এইবার বুঝতে পারলেন, একমাত্র এই পুত্রটির প্রতি তাঁর কী মমতা! কোথায় প্রতাপচাঁদ। একদিন এক মুসলমান আমলা এসে জানালেন, প্রতাপচাঁদের খবর তিনি জানেন। তিনি রাজমহলে আছেন। সঙ্গে সঙ্গে রাজকর্মচারীদের পাঠানো হল। তাঁরা প্রতাপচাঁদকে ধরে আনলেন। রাজবাড়িতে এলেও তাঁর বিমর্ষতা গেল না। তেজচাঁদ রোজ পুত্রকে কাছে বসিয়ে আদর করতেন, বোঝাতেন। প্রতাপ নিরুত্তর।
একদিন সকালে উঠে প্রতাপ খানসামাদের বললেন, আজ আমি নতুন মহলে চান করব। তিনি শখ করে একটি হামাম তৈরি করিয়েছিলেন। সেটি একবারও দেখতে যাননি। সেদিন কী খেয়াল হল! খানসামারা সেখানকার বিভিন্ন প্রণালীতে জল ভরে দিলেন। সবকটা ফোয়ারা খুলে দিলেন। জলের শব্দ বাইরে থেকে শোনা যেতে লাগল। প্রতাপচাঁদ তাঁর সাধের স্নানঘরে প্রবেশ করলেন। প্রায় এক প্রহর হয়ে গেল, তখনও তিনি বেরোলেন না। যখন বাইরে এলেন তখন চোখ দুটো টকটকে লাল, সারা শরীর কাঁপছে।
বিকেলেই রাজবাড়ির বাইরে খবর ছড়িয়ে পড়ল–প্রতাপচাঁদ ভীষণ অসুস্থ। ডাক্তার-বদ্যির আসা যাওয়া। একজন মুসলমান চিকিৎসক প্রতাপের খুব প্রিয় ছিলেন। তিনি তাঁরই কথা শুনতে লাগলেন। অসুখ দিন দিন বেড়েই চলল। শেষে বর্ধমানের সিভিল সার্জেন ডাক্তার কুলটার এলেন। খবর বেরোলসায়েব ডাক্তার কোনও ব্যবস্থা না করেই চলে গেছেন। ঘটনাটা ঠিক নয়, ডাক্তার কুলটার প্রতাপের কপালে দশ-বারোটা জোঁক বসাতে চেয়েছিলেন। বৃদ্ধ রাজা ও প্রতাপচাঁদ–দুজনেই আপত্তি জানানোয় ডাক্তার রাগ করে চলে গেছেন। সেকালের ডাক্তারদের প্রায় সংস্কারে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল–সব ব্যাপারেই জোঁক প্রয়োগ। ইংল্যান্ডে ডাক্তারদের একটা নামই হয়ে গিয়েছিল লিক অর্থাৎ জোঁক।
সেইদিনই বিকেলের দিকে প্রতাপচাঁদ বললেন, আমার গঙ্গাযাত্রার ব্যবস্থা করো। এত তাড়াতাড়ি তিনি চলে যাবেন এমন কারওরই মনে হল না। অবস্থা অতটা খারাপ নয়। কবিরাজ রাজবল্লভ এলেন। নাড়ি দেখে গঙ্গাযাত্রায় সায় দিলেন। প্রতাপকে নিয়ে যাওয়া হল কালনায়। সঙ্গে বৃদ্ধ মহারাজও রয়েছেন। আত্মীয় স্বজনদের কেউই গেলেন না; স্ত্রী লোকরা তো নয়ই। কালনায় পৌঁছে তাঁরা কয়েকদিন রাজবাড়িতে রইলেন। এইবার শেষ প্রহর। উপস্থিত। একদিন রাত দেড়টার সময় তাঁকে পালকি করে গঙ্গার তীরে নিয়ে যাওয়া হল। ঘাটটি ঘেরা হল কানাত দিয়ে। প্রতাপের দেহ অন্তৰ্জলিতে। গঙ্গার ঘাটে ছোটখাটো একটা ভিড়। সকলেই কানাতের বাইরে। ঘোর অন্ধকার। আট-দশটা মশাল জ্বলছে। একটা বড় জায়গার অন্ধকার এই আলোতে তেমন কাটছে না। জলের ধারে একটি তাঁবু। সেখানে ঘনিষ্ঠ কয়েকজন বসেছেন। পৌষ মাস, প্রচণ্ড ঠান্ডা। রাত দুটো প্রতাপ চলে গেলেন। রাত তিনটেয় চিতা জ্বলে উঠল। রাজা তেজচাঁদ বর্ধমান যাত্রা করলেন।
ভিন্ন ইতিহাসে বলা হচ্ছে, প্রতাপচাঁদ যখন মরণাপন্ন তখন তেজচাঁদের শ্যালক ও শ্বশুর পরাণচাঁদ মহারাজের ষষ্ঠ মহিষী অর্থাৎ তাঁর ভগ্নী কমলকুমারীর সাহায্যে জীবন্মত প্রতাপচাঁদকে সকার করার উদ্দেশে কালনার গঙ্গার তীরে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু চিতায় তুলে দাহ করার আগেই প্রবল ঝড়বৃষ্টি শুরু হল। পৌষের রাত। শ্মশান যাত্রীরা শবদেহ ফেলে রেখে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে স্থান ত্যাগ করলেন। দুর্যোগ থেমে যাওয়ার। পর এসে দেখলেন লাশ নেই। প্রতাপচাঁদের দুই স্ত্রীকে বিধবার বেশ ধারণ করানো হল। এইবার পরাণচাঁদের দ্বিতীয় চাল। তিনি তাঁর ভগ্নী মহারানি কমলকুমারীকে দিয়ে তেজচাঁদ বাহাদুরকে দত্তক পুত্র গ্রহণের জন্য চাপ দিতে লাগলেন। মহারাজা কিছুতেই দত্তক গ্রহণ করবেন না। তাঁর স্থির বিশ্বাস–প্রতাপ ফিরবেই। পরাণচাঁদ ও কমলকুমারী বোঝালেন, আপনার বয়েস হয়েছে। হঠাৎ মারা গেলে উত্তরাধিকারীর অভাবে পুরো রাজতৃটাই সরকারের খাস হয়ে যাবে। তিনি চুনীলাল মতান্তরে কুঞ্জবিহারীকে দত্তক নিতে বাধ্য হলেন। রাজার মৃত্যুর পর মাহতাবচাঁদ বাহাদুর নামে বর্ধমানের সিংহাসনে অভিষিক্ত হলেন। রাজা হিসেবে তিনি অপূর্ব দক্ষতার পরিচয় রেখে গেছেন। প্রতাপের মৃত্যুর ঠিক চোদ্দো বছর পরে হঠাৎ এক সাধুর আবির্ভাব। বর্ধমান ইতিমধ্যে অনেক বদলে গেছে। ইংরেজরা ভালো ভালো রাস্তা তৈরি করেছেন। ধারে ধারে বিলিতি ফুলের বাগান। কৃষ্ণসায়রের পাড় ঝকঝকে তকতকে। জঙ্গল কেটে সাফ। জায়গায় জায়গায় সুন্দর সুন্দর উদ্যান। সেইসব উদ্যানের নামও খুব আকর্ষণীয়। রাজবাড়ির বাইরেটা অপরিষ্কার হলেও ভেতরে অনেক নতুন মহল তৈরি হয়েছে। চিড়িয়াখানাটা নেই। সন্ন্যাসী সোজা রাজবাড়িতে প্রবেশ করলেন। চারদিক ঘুরে ঘুরে দেখলেন। কর্মচারীরা সব দেখেও কিছু বলছেন না। সন্ন্যাসীও নির্বাক। তিনি চলে এলেন বারমহলে। বহুঁকাল মেরামত হয়নি। দু-একটি দরজা ভাঙা। জায়গায় জায়গায় পলেস্তারা খসে পড়েছে। তিনি ঠিক করলেন–এইখানেই থাকবেন। এইবার কয়েকজন রাজকর্মচারী এসে তাঁকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিলেন।
নির্বিকার সন্ন্যাসী গোলাপ বাগে গিয়ে হাজির হলেন। ভেতরে ঢুকলেন না, গেটের একপাশে বসে রইলেন। অদূরেই গোপীনাথ ময়রার দোকান। তাঁর দিকে চোখ পড়তেই ময়রা বলে উঠলেন, একি আমাদের ছোট মহারাজ না! সন্ন্যাসী তাকালেন। গোপীনাথ ছুটে এসে গলায় কাপড় দিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে জোড়হাতে দাঁড়িয়ে রইলেন। সন্ন্যাসী তাঁর সঙ্গে কথা বলছেন। দেখতে দেখতে ভিড় জমে গেল। শহরের সর্বত্র দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ল। সংবাদ–ছোট মহারাজ ফিরে এসেছেন। চতুর্দিক থেকে পিলপিল করে লোক আসতে লাগল। ছোট মহারাজের রানিদের কানে খবরটা যেতেই তাঁরা পুরোনো এক দাসীকে পাঠালেন। দাসী ফিরে এসে চোখের জল মুছতে মুছতে বললে, আর সে বর্ণনাই, সে মূর্তি নাই, কিন্তু গাল ভরা সেই হাসিটি রয়েছে। ছিলেন মহারাজাধিরাজ আজ সন্ন্যাসী। একেই বলে মা, যে রাজ্যে রাজা ছিলেন, সেই রাজ্যে মেগে খেলেন। রাজবাড়ির পুরনো আমলারা দেখতে এলেন। তাঁদের একজন–মুহুরী, কুঞ্জবিহারী ঘোষ। রাজবাড়িতে ফিরে এসে পরাণবাবুর মেজছেলে তারাচাঁদকে বললেন, বাবু, আর দেখতে হবে না। আমাদের ছোট মহারাজ সত্যি, সত্যি ফিরে এসেছেন। তারাচাঁদ এই খবরটি বাবাকে জানালেন। পরাণবাবু সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন লেঠেলকে পাঠালেন। তাদের হম্বিতম্বিতে সন্ন্যাসী সেই জায়গা ছেড়ে চলে গেলেন কাঞ্চননগরে। পরাণবাবু ছাড়ার পাত্র নন, আবার লেঠেল পাঠালেন। তারা সন্ন্যাসীকে দামোদর পার করিয়ে দিয়ে এল। কুঞ্জবিহারীর চাকরি গেল।
সেই ভবিষ্যদ্বাণী ফলে গেল অক্ষরে অক্ষরে। পরাণবাবুর ছোটছেলে তেজচাঁদ বাহাদুরের। মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসলেন। প্রতাপচাঁদ রাজার লেঠেলদের তাড়া খেয়ে অবশেষে এলেন বর্ধমান রেল স্টেশনের উত্তরে একটি পরিত্যক্ত স্থানে। ধুনি জ্বালিয়ে কিছুদিন থাকার পর তাঁর একটি ডেরা তৈরি হয়ে গেল। তখন পরাণচাঁদ জেলাশাসককে হাত করে সন্ন্যাসীকে আবার তাড়ালেন। তুলে দিয়ে এলেন কালনার রাস্তায়। রটিয়ে দিলেন, এ মিথ্যেবাদী, একটা পয়লা নম্বরের জোচ্চোর। সাধু আর ফিরলেন না। এইবার সাধু যে জায়গায় ধুনি জ্বালিয়ে বসলেন পরবর্তীকালে সেই অঞ্চলটির নাম হল বাজে প্রতাপপুর। প্রতাপচাঁদের বন্ধু-বান্ধবের অভাব ছিল না। বিষ্ণুপুরের রাজা ক্ষেত্রমোহন সিংহ তাঁর ঘনিষ্ঠ ছিলেন। প্রতাপচাঁদের দাবি প্রমাণ করার জন্য তিনি হুগলি কোর্টে একটি মামলা দায়ের করলেন। মামলা চলল বেশ। কয়েকবছর। বহু সাক্ষী পক্ষে-বিপক্ষে সাক্ষ্য দিলেন। মামলা দাঁড়াল না। প্রতাপচাঁদ রাজপদের অধিকার চিরতরে হারালেন।
সন্ন্যাসী প্রতাপচাঁদ মানুষের খুব প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর সৌম্য চেহারা। সুমিষ্ট ব্যবহার, বহুরমণী তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। প্রতাপচাঁদকে কয়েক বছরের জন্য জেলেও যেতে হয়েছিল। তিনি শান্ত গলায় বিচারপতিকে একটি সুন্দর প্রশ্ন করেছিলেন–আমি এখনও বুঝতে পারলুম না, কী অপরাধে আপনি আমাকে দণ্ড দিলেন। বিচারপতি বলেছিলেন, তোমার আসল নাম আলোকশা। মহারাজাধিরাজ প্রতাপচাঁদ বলে লোক জুটিয়েছ। রাজ্যের। শান্তি নষ্ট করেছ। আমি তোমাকে কয়েক বছরের জন্য জেলে পাঠালুম। ১৮৩৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের যে দিনে তিনি কারামুক্ত হলেন সেদিন হুগলিতে এক মহাসমারোহ, কলকাতা থেকে বহু সম্রান্ত ব্যক্তি তাঁকে নিতে এসেছিলেন। পরের দিনটিতে ছিল অর্ধোদয় যোগ। সেই উপলক্ষে বর্ধমান আর বাঁকুড়ার বহু পুণ্যার্থী হুগলি ও ত্রিবেণীতে সমবেত হয়েছিলেন। তাঁরাও সংবর্ধনায় যোগ দেন। পঞ্চকোটের রাজা ও বিষ্ণুপুরের রাজা–দুজনেই এসেছিলেন। তাঁরা জেলখানার গেটে হাজির হলেন। অঞ্চলের ধনীরা দেশি বাদ্য, ইংরেজি বাদ্য, হাতি, ঘোড়া, রেসালা নিয়ে জেলখানার সামনে হাজির। প্রতাপচাঁদ বেরনো মাত্রই হাতির ওপর স্থাপিত নহবত বেজে উঠল। চতুর্দিকে কাড়ানাকাড়ার শব্দ, হরিধ্বনি, তিন-চার দল ইংরেজি বাদ্য বেজে উঠল। সবাই মিলে প্রতাপচাঁদকে পালকির সুখাসনে বসালেন। পালকিবাহকদের কাঁধে চারজন বালক, চামর ব্যজন করছে। শতশত পতাকা আগে আগে। নগর প্রদক্ষিণ শেষ করে সাধু জাহাজে উঠলেন। চলে এলেন কলকাতায়। তাঁর থাকার। জায়গা নির্ধারিত হয়েছিল। রাধাকৃষ্ণ বসাকের বাড়িতে।
প্রথমে কলকাতার চাঁপাতলা। সেখান থেকে প্রতাপচাঁদ এলেন কলুটোলার গোবিন্দ প্রামাণিকের বাড়িতে। এই ব্যক্তির আশ্রয়ে দু-তিনমাস থেকে তাঁকে নিঃস্ব করে দিলেন। গোবিন্দবাবু এই জাল রাজার ওপর জুয়ার দান ধরেছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল তিনি আসল প্রতাপচাঁদ। যথাসময়ে রাজ্য ফিরে পাবেন এবং তাঁরও বরাত খুলে যাবে। প্রতাপচাঁদ এরপর গেলেন শ্যামপুকুরে। কিছুদিনের মধ্যেই ইংরেজ সরকার লাহোরের লড়াইতে জড়িয়ে পড়ল। সরকারের নজর পড়ল প্রতাপচাঁদের ওপর। তিনি কোম্পানির রাজ্য ছেড়ে পালিয়ে গেলেন চন্দননগরে ফরাসিদের আশ্রয়ে। কয়েকবছর থাকার পর এলেন শ্রীরামপুরে। এইখানে তিনি হলেন ঠাকুর। সেইরকম তাঁর সাজপোশাক চালচলন। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় বেশ্যারা এসে পঞ্চপ্রদীপ আর ঘণ্টা বাজিয়ে তাঁকে আরতি করত। তিনি জ্যান্ত ঠাকুর হয়ে সিংহাসনে বসে থাকতেন। অনেকেই ভাবলেন রাজ্যহারা রাজার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।
কিন্তু তাঁর কথাবার্তা ও চালচলনে পাগলামির কোনও চিহ্ন ছিল না। বরং অসাধারণ বুদ্ধিমান ও সর্বশাস্ত্রজ্ঞ এক ব্যক্তি। বিলেতের রাজনীতিতে তাঁর অসাধারণ জ্ঞান। সমস্ত দেশের ইতিহাস তাঁর নখাগ্রে। সবচেয়ে ভালো বুঝতেন রুশ পলিটিক্স। বেদান্ত শাস্ত্রেও মহাপণ্ডিত।
এইটা তাঁর একটা দিক। আর অন্যদিকে বিচিত্র তাঁর পাগলামি। কখনও তিনি নিজেকে শালগ্রাম শিলা মনে করতেন। সর্বদা বসে থাকতেন ঝারায়। লোকের সচন্দন পুস্পাঞ্জলি নিতেন। পূজা গ্রহণ করতেন, বৈকালিও খেতেন। অনুগামীদের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যা বেশি হলেও পুরুষের সংখ্যাও কম ছিল না। বাবাজিরা এসে তাঁর দরজায় পড়ে থাকতেন। স্ত্রীলোকদের ধারণা হয়েছিল এই মানুষটি সাক্ষাৎ দেবতা। তিনি যে মন্ত্র দিতেন তা বিষ্ণু। মন্ত্রও নয়, শক্তি মন্ত্রও নয়। তাঁর দীক্ষা দেওয়ার পদ্ধতি ও অর্চনা করার পদ্ধতি একদম ভিন্ন। এই নতুন ধর্মটি পরবর্তীকালে হয়ে দাঁড়াল তঙ্কালের বিখ্যাত ঘোষপাড়ার দল অর্থাৎ কর্তাভজা সম্প্রদায়। এখন এই লেখক যেখানে বসবাস করেন তাঁর দূরেই ময়রাডাঙার একটি বাড়িতে ১৮৫২ অথবা ৫৩ সালে এই সাধুর জীবনাবসান হয়। সেই সময় তিনি সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ। সঞ্জীবচন্দ্র লিখছেন, তাঁহার যাত্রার সময় চক্ষের জল মুছিবার কেহ ছিল না।