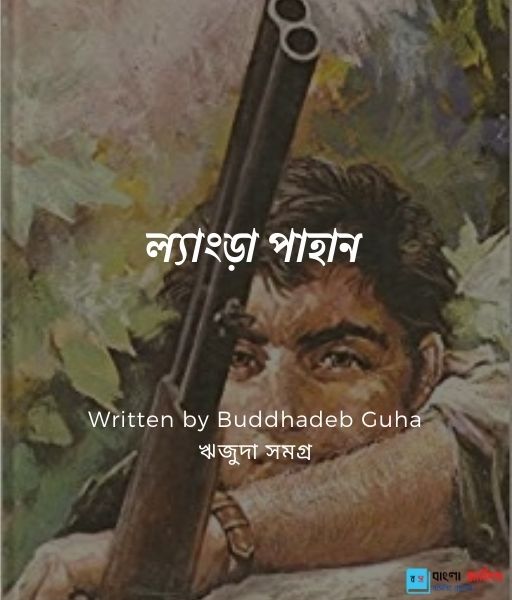মউলির রাত
একপাশে গোন্দা বাঁধ, অন্য পাশে শালের জঙ্গল, টাঁড়; বড় বড় মহুয়া ও অশ্বত্থ গাছ। মধ্যে দিয়ে লাল পাথুরে পথটা করোগেটেড শিটের মতো ঢেউ খেলানো। সেই পথ ছেড়ে পায়ে-চলা পথে তিতির আর কালিতিতিরের ডাক শুনতে শুদতে খোয়াইয়ে ও টাঁড়ে টাঁড়ে হেঁটে গেলে একটু এগিয়ে গিয়েই বোকারো নদী পড়ে। নদীর হাঁটুজল পেরিয়ে অন্য পাশের খাড়া পাড় ডিঙিয়ে আরও আধ মাইলটা গেলেই কুসুভা গ্রাম।
প্রথম আমার সঙ্গে কাড়ুয়ার এখানেই দেখা হয়। সেদিনটার কথা এখনও স্পষ্ট মনে পড়ে।
গাঁয়ের সীমানায় ও কতগুলো কালো ছাগল চরাচ্ছিল। এক ফালি কাপড় মালকোচা মেরে পরা। হাতে একটা ছোট লাঠি। মাথার চুল কদম-ছাঁটে ছাঁটা–পিছনে একটা আধহাত লম্বা টিকি।
ছেলেটাকে দেখতে একেবারে কাকতাড়ুয়ার মতো।
আমাদের দেখতে পেয়েই কাড়ুয়া দৌড়ে এল। তাড়াতাড়িতে আসতে গিয়ে একটা ছাগল-ছানার পা মাড়িয়ে দিল। সেটা ব্যাঁ–অ্যা–অ্যা করে ডেকে উঠল।
কাড়ুয়া যখন এগিয়ে আসছিল, ঠিক সেই সময় দেখি ওর পিছনে পিছনে একটা এক-ঠ্যাঙা সাদা গোবক লাফিয়ে লাফিয়ে আসছে।
কাড়ুয়া এসে কোমর ঝুঁকিয়ে বলল, পরনাম।
গোপালের পুরোনো সাকরেদ ও। গোপাল আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল।
কাড়ুয়ার কথা এত শুনেছি যে, নতুন করে শোনার কিছু ছিল না। আমাদের দেখামাত্র ছাগলদের আপন মনে চরতে দিয়ে ও আমাদের সঙ্গে হেঁটে চলল। খোঁড়া বকটাকে কোলে তুলে নিল।
গোপাল বকটার গায়ে হাত ভুলিয়ে আদর করে দিয়ে বলল, কেয়ারে বগুলা, আচ্ছা হ্যায়?
বগুলা মুখ ঘুরিয়ে গোপালের দিকে তাকাল।
দেখলাম, তার এক চোখ কানা।
গোপাল বলল, এ হচ্ছে কাড়ুয়ার বুজুম-ফ্রেণ্ড।
কাড়ুয়াদের গ্রামে একটা বড় দাঁতাল শুয়োর খুব অত্যাচার আরম্ভ করেছে। কাড়ুয়াও শিকারী। ওর নিজের একটা গাদাবন্দুক আছে। গোপাল সেটার নাম দিয়েছে যন্তর।
কাড়ুয়ার বন্দুকটা সম্বন্ধে একটু বলে নিই। বন্দুকটা কথাটথা বলত কাড়ুয়ার সঙ্গে। একেবারে মন-মৌজী বন্দুক। রাতে হয়তো ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে– কাড়ুয়ার মাটির ঘরের দেওয়ালে বন্দুকটা টাঙানো আছে– হঠাৎ বন্দুক ফিসফিস করে কাড়ুয়াকে বলল, শটিক্ষেতোয়ামে শুয়ার আওল বা।
কাড়ুয়া শুনতে না পেলে আবারও বলল আর একটু জোরে, আর অমনি কাড়ুয়া হুম্মচকে তিন অংগুলি ককে বন্দুক নিয়ে বেরিয়ে পড়ল শটিক্ষেতের উদ্দেশে।
হুম্মচকে মানে বাংলায় কী বলব জানি না। ধরো, বলা যায়, তেড়ে-খুঁড়ে। আর তিন অংগুলি কত্সকে মানে হচ্ছে, জোরসে তিন আঙুল বারুদ গাদা বন্দুকে পুরে। জানোয়ার বুঝে ঐ বন্দুকে বারুদ গাদাগাদির তফাত হয়। মুরগী মারতে এক আঙুল, কোটরা হরিণ মারতে দু আঙুল, তার চেয়ে বড় জানোয়ার মারতে তিন আঙুল। আরও বেশি আঙুল গাদলে অনেক সময় বন্দুকের মুঙ্গেরী নল ফেটে গিয়ে শিকারীই হয়তো আঙুল-হারা হয়ে যায়। শিকার-ফিকার করলে এসব রিসক্ একটু থাকেই। কী করা যাবে!
আমরা গিয়ে গাঁয়ের তেঁতুলতলায় বসলাম, আসোয়ার ঘরের পাশে। খিচুড়ি চাপালাম। খেয়ে-দেয়ে ঘুম। তারপর সন্ধের পর শুয়োরের কল্যাণে লাগা যাবে।
.
কাড়ুয়া স্বভাবকবি। ইতিমধ্যেই শুয়োরটার উপরে একটা কবিতা বানিয়ে ফেলেছে দেখলাম।
“আর এ-এ শুয়ারোয়া
ব–ড়কা শুয়ারোয়,
কা–কহি তুমহারা বাত
ছুপকে ছুপকে গাওমে ঘুষতা
হর শনি–চ্চর রাত।
কালা বিলকু বদন তুমহারা
হাসসে ভি কালা, কোই বাত্?
ভোগল-ভুচুন্দর বড়কা ছুছন্দর
কিঁউ মজা হামারি সাথ?
বোলা লিয়া ম্যায় দোস্তলোগোঁকো
নিকা লেগা তেরী দাঁত,
গোপালবাবু লায়া ভোপাসে বন্দুক
আজ-হি আখীর কা রাত।”
গোপাল বলল, সাবাস্ সাবাস্ সাবাস্! বহত্-খুউব।
তারপর ও বলল, কাড়ুয়া, তোকে নিয়ে আমিও একটা কবিতা লিখেছি, শোন্ বলি।
কাড়ুয়া টিকিটা এদিক-ওদিক নাড়িয়ে কুচকুচে কালো মুখে সাদা দাঁতের সুন্দর হাসি হেসে বলল, বোলো গোপালবাবু, বোলো–
গোপাল ছড়ার মতো করে ছন্দ মিলিয়ে বলল :
“আরে এ–এ কাড়ুয়ারে
কাক–হি তাড়য়ারে,
তুমহারা নেহি কোই জওয়াব–
বগুলাসে দোস্তি, খাতা হায় জাস্তি
তিতিরকা বনা-হুঁয়া কাবাব।
শোচ্ সমঝ কর, শিকার তু খেলনা,
কই রোজ ঝামেলামে গিড়ে গা–
বড়কা শুয়ারোয়া দাঁতোয়া ঘুষানেসে
দাওয়াই ত হিয়া নেহি মিলেগা।
বহত সামহাকে কদম বাড়হা তু
জলদি বাজী নেহি, আইস–তা–
তিন–অংগলি ককে,
হু-হু-হু হুম্মিচ্কে–
শুয়ার্কা পেট তব্হি ফাসতা।”
আমি তো দুই কবিয়ালের কবিতা শুনে থ!
সন্ধের পর পরই গোপাল আর কাড়ুয়ার সঙ্গে নয়াতালাওর পাশের শটিক্ষেতের দিকে রওনা হলাম আমরা।
বর্ষাকাল। আকাশে মেঘের ঘনঘটা। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। মেঘগর্জনের সঙ্গে। সেই বিজলীতে চতুর্দিকের জঙ্গল আর টাঁড় রুপোলি আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে।
আমরা গ্রামের দেওতার ঠাঁই পেরিয়ে, ঝুরিওয়ালা অশ্বথ গাছটার পাশ দিয়ে অনেকখানি হেঁটে গিয়ে নয়াতালাওর পাশের শটিক্ষেতে গিয়ে উপস্থিত হলাম।
কাড়ুয়া দেখাল শুয়োটা সাধারণত কোন দিক দিয়ে এসে ঢোকে শটিক্ষেতে।
আমরা তিনজনে ভিজে মাটির উপরেই সাপ-খোপ বাঁচিয়ে শটিক্ষেতের আড়ালে গা-লুকিয়ে বসলাম।
গোপাল মারবে আগে। কোন এক মহারাজার পরিবারের এক লোকের কাছ থেকে সদ্য-কেনা বারো বোরের ওভার-আণ্ডার দশ-হাজারী বন্দুক দিয়ে। গোপালের নিবেদনের পর, কাড়ুয়া তার মুঙ্গেরী গাদা বন্দুক দিয়ে মহার্ঘ্য নিবেদন করবে।
আমি দর্শক।
বসে বসে মশার কামড় খেয়ে খেয়ে সারা গা-মুখ সিন্দুরের মতো লাল হয়ে উঠল। শুয়োরের বাচ্চার কোনও পাত্তা নেই।
বোধ হয় ঘণ্টা দুয়েক বসে থাকার পর তিনি এলেন। দাঁতের জোরে এবং লাথি মেরে মেরে ভিজে নরম মাটি ফুলঝুরির মতো ছিটোতে ছিটোতে এবং শটিগাছ ও কচুগাছ উপড়োতে উপড়োতে আসতে লাগলেন।
জঙ্গলের দিক থেকে একটা ভিজে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছিল। গা শিরশির করছিল। চারধারে মুখ ঘুরিয়ে দেখলাম, আমার পেছনে একটা পন্ন গাছ আছে। আমিই একমাত্র নিরস্ত্র।
শুয়োরটা দেখতে দেখতে একেবারে কাছে এসে গেল।
এমন সময় মেঘ ফুঁড়ে এক ফালি চাঁদ বেরোল। সেই চাঁদের লাজুক আলোয় শুয়োরটার ইয়া-ইয়া দাঁত দুটো চৰ্চ করছিল।
গোপাল ভাল করে নিশানা নিয়ে গুলি করল। কিন্তু গুলি হল না। কট করে আওয়াজ হল একটা।
আওয়াজটা শুনেই শুয়োরটা শটি খাওয়া থামিয়ে এদিকে মুখ তুলল।
গোপাল আবার মারল। আবারও কটু। নট-কিচ্ছু।
এবার শুয়োরটা আস্তে আস্তে আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল।
কলকাতা থেকে আসার আগে নতুন গুলি নিয়ে এসেছিল গোপাল চৌরঙ্গীর এক দোকান থেকে। দু-দুটো এল-জির একটাও ফুটল না। দোকানদার গোপালের বন্ধু। বিনি পয়সার গুলি তো। বড় ভালবাসার গুলি।
আবারও গুলি ভরার জন্যে ও যেই বন্দুকটা খুলেছে, ইজেকটরটা গুলি দুটোকে পটাং শব্দ করে বাইরে যেই ছুঁড়েছে, সঙ্গে সঙ্গে রে–রে করে বড়কা শুয়ারোয়া সটান আমাদের দিকে একটা ট্যাঙ্কের মতো তেড়ে এল।
আর আমি ওখানে থাকি?
এক দৌড়ে আমি পন্নন গাছে এসে উঠলাম।
ওদের ঘাড়ের কাছ দিয়ে আমার হুড়মুড় করে দৌড়ে পালানোর শব্দে গোপাল ও কাড়ুয়া চমকে উঠে ভাবল, অন্য একটা শুয়োর বুঝি অন্যদিক থেকে যুঁ মারার জন্যে তেড়ে আছে।
ওরা ব্যাপারটা কী বোঝার আগেই আমি গাছে।
ততক্ষণে শুয়োরটাও ওদের একেবারে কাছে এসে গেছে। গোপাল আর গুলি ভরার সময় পেল না। দেখলাম কাড়ুয়া ওর বন্দুকটাকে শুয়োরের দিকে বাগিয়ে ধরে কখন শুয়োরের নাকের সঙ্গে ওর বন্দুকের নলের ঠেকাঠেকি হয় সেই অপেক্ষায় প্রস্তুত হয়ে রইল। সেকেন্ডের মধ্যে শুয়োরও এসে পৌঁছল ঘোঁত-ঘোঁত শব্দ করতে করতে আর ক রি বন্দুকও ছুটল।
দূর থেকে আবছা-আলোয় ঘটনাটা কী ঘটল বুঝলাম না। কিন্তু মারাত্মক কিছু যে একটা ঘটল, সেটা বুঝলাম। দেখলাম, তিনটে জিনিস তিনদিকে ছিটকে পড়ল আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে।
শুয়োরটা উল্টে পড়ে শটিক্ষেতে অনেকক্ষণ হাত-পা ছোঁড়াছুঁড়ি করে গুচ্ছের শটিগাছ ভেঙে নষ্ট করে মাটি ছিটিয়ে একাক্কার করল। অনেকক্ষণ পর একেবারে স্থির হল।
কিন্তু শুয়োর-শিকারীরা নড়েও না, চড়েও না।
বড়ই বিপদে পড়লাম।
পরিস্থিতি শান্ত হলে, গাছ থেকে নেমে আমি পা টিপে টিপে ওদের কাছে গিয়ে পৌঁছলাম।
গিয়ে যা দেখলাম, তা বলার নয়।
গোপাল তার ওভার-আণ্ডার বন্দুকের আণ্ডারে শুয়ে আছে। তার নাকটা বারুদে কালো।
কাড়ুয়া অজ্ঞান–তার সমস্ত মুখ, ডান হাত পুড়ে যাওয়ার মতো হয়ে গেছে।
আমি ওর গায়ে হাত ছোঁয়াতে, গোপাল কোঁকাতে কোঁকাতে উঠে বলল, কাড়ুয়ার বন্দুকের নল ফেটে গেছে।
আমি আতঙ্কিত গলায় বললাম, ক-আংগলি গেদেছিল?
গোপাল বলল, ও জানে!
এমন সময় কাড়ুয়া চার হাত-পায়ে কোনওরকমে উঠেই হাউ-হাউ করে কাঁদতে লাগল, হামারা বন্দুকোয়া, হামারা বন্দুকোয়া বলে।
গোপাল ধমক দিয়ে বলল, প্রাণে বেঁচে গেছিস, এই-ই ঢের; আর বন্দুকের জন্যে কেঁদে কাজ নেই।
কাড়ুয়া তবু কাঁদতে লাগল। বলতে লাগল, হাকো ভি এক গোলি ঠুক্ দেও, হাভি হামারা বন্দুককা সাথ মরনা চাহতা হ্যায়।
গোপাল কাড়ুয়ার মুখের দিকে অনেকক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল।
তারপর বলল, হামারা এক্কো গুলি নহী ফুট। শুয়ারকাই মারনে নহী শে, তুমকো মারেগা কৈসে?
.
মউলির রাত
পাকদণ্ডীটা সামনে বড় খাড়া।
দুপুরে ঝরনার পাশে খিচুড়ি ফুটিয়ে খাওয়ার পর থেকে প্রায় পাঁচ মাইল হেঁটেছি আমি আর জুডু; তাও প্রায় বেশির ভাগই চড়াইয়ে-চড়াইয়ে। উত্রাই প্রায় পাইনি বলতে গেলে।
এদিকে বেলা যেতে আর বেশি দেরি নেই। পশ্চিমের দরের পাহাড় দুটোর মাঝখানে যে একটা ত্রিকোণ ফাঁক, সূর্যটা সেই ফাঁকের মধ্যে কিছুক্ষণের জন্যে একটা পাঁচনম্বরী লাল ফুটবলের মতো স্থির হয়ে রয়েছে। বলটা গড়িয়ে পাহাড়ের ঢালে নামলেই ঝুপ করে আলো কমে যাবে।
কিন্তু রাতের মতো তাঁবু খাটাবার জায়গার হদিস এখনও পর্যন্ত পাওয়া গেল না।
হঠাৎ জুডু বলল, এখানেই থাকব। আর যাব না।
এখনও যা আলো আছে, তাতে মিনিট পনেরো-কুড়ি যাওয়া যেত, কিন্তু হঠাৎ জুডুর এমন জোর গলায় এখানেই থাকব– কথাটার মানে বুঝলাম না।
এতক্ষণ ও আমাদের পাতলা তাঁবু, আমার স্লিপিং ব্যাগ, ওর কম্বল ও রসদের ঝুলিটা কাঁধে নিয়ে আমার পেছন-পেছন আসছিল।
হঠাৎ যেখানে ছিল ও সেখানেই থেমে গেল।
দাঁড়িয়ে পড়ে, জায়গাটা ভাল করে দেখলাম।
তাঁবু যে ফেলা যায় না, তা নয়; তবে এর চেয়েও ভাল জায়গা নিশ্চয়ই পাওয়া যেত। জায়গাটা একটা পাহাড়ের একেবারে গায়ে। পুবে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রীতে উঠে গেছে ঘন জঙ্গলাবৃত পাহাড়টা। পশ্চিমে সোজা গড়িয়ে গিয়ে নীচে মিশেছে একটা উপত্যকায়। উপত্যকায় গভীর জঙ্গল। কত রকম যে গাছগাছালি তার লেখাজোখা নেই। সেই উপত্যকার গভীরে-গভীরে বয়ে গেছে একটা পাহাড়ী নদী। জুডু তার নাম জানে না।
আসলে ওড়িশার দশপাল্লা রাজ্যের বিড়িগড় পাহাড়ের এই অঞ্চলটা জুড়ুরও যে ভাল জানা নেই, তা আমি জানতাম। আমার তো নেই-ই।
আমি আর জুড় কাল বিকেল থেকে সেই বিরাট শম্বরটার খুরের দাগ দেখে দেখে পেছন-পেছন যাচ্ছি, কিন্তু এরকম অভিজ্ঞতা আমার কখনও হয়নি।
আমারও জেদ চেপে গেছে।
এরকম অতিকায় শম্বর আমার জীবনে দেখিনি আমি। দশ বছর বয়স থেকে জঙ্গলে ঘুরছি, তবুও। আমি তো কোন ছার, জুডু বলেছিল, সেও দেখেনি। এমন দাড়িগোঁফওয়ালা ও জটাজুট-সংবলিত শম্বর যে এই বিংশ শতাব্দীতেও কোনও জঙ্গলে থাকতে পারে, একথা বিশ্বাস করা শক্ত। আমার এবং আমার বন্ধু জর্জ ট্রব ও কেন্ ম্যাকার্থির পারমিটে একটা বাইসন, একটা শম্বর, একটা ভালুক ও একটা চিতা মারার অনুমতি ছিল। কিন্তু আজ সকালে একটা পাহাড়ী নদীর নালায় বসে যখন রোদ পোহাচ্ছিলাম তখন হঠাৎ তিনশ গজ দূরে পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে থাকা শম্বরটাকে দেখে আমার মাথা ঘুরে গেছিল। তখন আমার সঙ্গে রাইফেল ছিল না, থাকলে তক্ষুনি গুলি করতাম। তাই, জর্জ আর কেকে বলে, জুডুকে সঙ্গে নিয়ে পনেরো মিনিটের মধ্যে আমি বেরিয়ে পড়েছিলাম– শম্বরটাকে তার খুরের দাগ দেখে দেখে অনুসরণ করে।
আমার সঙ্গে থ্রি-সিক্সটিসিক্স বোরের একটি ম্যানলিকার রাইফেল ছিল। আজ বিকেলে শম্বরটাকে আর একবার পাল্লার মধ্যে পেয়েছিলাম। এক মুহূর্তের জন্যে। কিন্তু মুহর্তের মধ্যেই উচিত ছিল প্রথম দর্শনেই তাকে ভূপাতিত করা। রাইফেলটা আমার হাতের রাইফেল এবং নিখুঁত মার মারত। তখন কেন যে মারলাম না, এ-কথা ভাবলেই নিজের হাত কামড়াতে ইচ্ছে করছিল।
শম্বরটাও অদ্ভুত। এ পর্যন্ত অনেক জানোয়ারকে ট্র্যাকিং করেছি, আহত ও অনাহত, কিন্তু এমনভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গভীর থেকে গভীরতর, দুর্গম থেকে দুর্গমতর জঙ্গলে কোনও জানোয়ারই এরকম গা-ছমছম অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে আমাকে টেনে নিয়ে যায়নি। এমনভাবে বরাবর রাইফেলের পাল্লার বাইরেও কেউ থাকেনি। ট্র্যাকিং আরম্ভ করার পর বিকেলে সেই প্রথমবার যে তার চেহারা দেখেছিলাম, তারপর থেকে তার চেহারা সে আর একবারও দেখায়নি। দ্বিতীয়বার দেখা গেলে, সে যত দূরেই হোক না কেন, গুলি আমি নিশ্চয়ই করতাম।
হঠাৎ জুডু মালপত্রগুলো মাটিতে নামিয়ে রেখে নাক উঁচু করে বাতাসে কিসের যেন গন্ধ শুঁকতে লাগল কুকুরের মতো।
পরক্ষণেই দেখলাম, তার মুখটা ছাইয়ের মতো সাদা হয়ে গেছে।
আমি কাঁধে-ঝোলানো রাইফেলটাকে তাড়াতাড়ি রেডি-পজিশনে ধরে ওর মুখের দিকে তাকালাম।
ও কথা না বলে বাঁ হাত দিয়ে ধাক্কা দিয়ে রাইফেলের নলটাকে সরিয়ে দিল।
আমি অবাক হয়ে শুধোলাম, কী রে জুড়?
জুড়ু মুখে কথা না বলে শুধু দু পাশে মাথা নাড়তে লাগল জোরে জোরে। মাথা নাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওর দু চোখে ভয় ঠিকরোতে লাগল।
পরক্ষণেই মালপত্র কাঁধে তুলে নিয়ে বলল, বাবু, এখুনি চলো এখান থেকে পালাই। এখানে আর এক মুহূর্তও নয়।
আমি তেমনি অবাক হয়ে আবারও শুধোলাম, কী রে? একলা গুণ্ডা-হাতি? কিসের ভয় পেলি?
জুডু ফ্যাকাশে মুখে বিড়বিড় করে বলল, মউলি।
আবারও বিড়বিড় করে বলল, মউলি, মউলি, মউলি।
বলেই, পেছন দিকে দৌড় লাগাল।
আমি দৌড়ে গিয়ে ওর হাত ধরলাম।
ধমকে বললাম, কী, হলো কী তোর? আমার সঙ্গে তুই কি এই-ই প্রথম এলি জঙ্গলে? আমি সঙ্গে থাকতে তোর কোন জানোয়ারের ভয়?
ওড়িশার জঙ্গলে মউলি বলে কোনও জানোয়ার আছে বলে শুনিনি। প্রায় সব জানোয়ারেরই ওড়িয়া নাম আমি জানি, যেমন শজারুকে ওরা বলে ঝিংক, নীল গাইকে বলে ঘড়িং, মাউস-ডিয়ারকে বলে খুরান্টি। কিন্তু মউলি? নাঃ মউলি বলে তো কোনও কিছুর নাম শুনিনি!
ততক্ষণে জুডু থরথর করে কাঁপতে শুরু করেছে। ওর বুকে একটা জানোয়ারের সাদা হাড় ঝোলানো ছিল লকেটের মতো, কালো কারের সঙ্গে, সেটাকে মুঠো করে ধরে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, ঋজুবাবু, এক্ষুনি পালিয়ে চলো। আমরা মউলির এলাকায় এসে পড়েছি। এখানে থাকলে আমাদের দুজনের মৃত্যু অনিবার্য। ঐটা শম্বর নয়; মউলির দৃত। ও আমাদের ওর পেছনে-পেছনে দৌড় করিয়ে মউলির রাজত্বে এনে ফেলেছে। এর মানে আমাদের মরণ। এতে কোনও ভুল নেই।
আমি ওকে ধমকে বললাম, মউলি কী? আর তোর ব্যাপারটাই বা কী?
জুড় বলল, মউলি জঙ্গলের দেবতা, জানোয়ারদের দেবতা। জানোয়ারদের রক্ষা করেন মউলি। ওঁর রাজত্বে যে শিকারী ঢোকে, তাকে আর প্রাণ নিয়ে ফিরতে হয় না।
আমি এবার খুব জোরে ধমক দিয়ে বললাম, থামবি তুই? তোর মউলির নিকুচি করেছি আমি।
তারপর বললাম, শীগগিরি আগুন কর, কফির জল চড়া; তারপর রান্নার ব্যবস্থা কর। ততক্ষণে আমি তাঁবু খাঁটিয়ে নিচ্ছি।
মনে মনে বললাম, যত সব অশিক্ষিত কুসংস্কারাবদ্ধ জংলী লোক। জঙ্গলের দেবতা না মাথা। কত জঙ্গলে রাতের পর রাত কত অচেনা অজানা ভয়াবহ পরিবেশে কাটালাম, আর ও আমাকে মউলির ভয় দেখাচ্ছে!
জুডু হঠাৎ আমার দিকে একবার চকিতে চেয়েই, মালপত্র ফেলে রেখে সটান দৌড় লাগাল। পেছন দিকে।
রাইফেলটা হাতেই ছিল। আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, ওকে ভয় পাওয়ানোর জন্যে বললাম, জুডু, তোকে আমি গুলি করব, যদি পালাস।
কিন্তু জুডু তবুও শুনল না।
তখন মুহূর্তের মধ্যে জুড়ুকে সত্যি ভয় পাওয়াবার জন্যে আমি আকাশের। দিকে ব্যারেল তুলে একটা গুলি ছুঁড়লাম।
গুলির শব্দে জুডু থমকে দাঁড়াল। ভাবল, ওর দিকে নিশানা করেই বুঝি বা গুলি ছুঁড়েছিলাম।
আমি বললাম, এক্ষুনি ফিরে আয়, নইলে তোকে এই জঙ্গলেই মারব আমি, তোর মউলি তোকে মারবার আগে।
জুডু কাঁপতে কাঁপতে, মউলির ভয়ে না আমার ভয়ে জানি না, ফিরে এল।
ওকে ভয় দেখানো ছাড়া আমার কোনও উপায় ছিল না। কারণ, জঙ্গল-পাহাড়ের এদিকটা আমার একেবারেই অচেনা। আমি একা-একা কিছুতেই আমাদের ক্যাম্পে ফিরতে পারতাম না। সেখান থেকে বহু দূরে চলে এসেছিলাম আমরা। সঙ্গের রসদও প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। শুধু এক রাতের মতো তৈরি হয়ে এসেছিলাম। জুড়ু চলে গেলে আমার সত্যিই বিপদ হবে।
বাধ্য হয়ে জুড়ু এবার আগুন করল, কফির জল চাপাল, তারপর তাঁবুটা খাটাতে ও আমাকে সাহায্য করল।
ততক্ষণে অন্ধকার হয়ে গেছে। প্রথম রাতেই চাঁদ ওঠার কথা ছিল, কিন্তু আমরা মাথা-উঁচু পাহাড় ঘেরা এমন একটা খোলের মধ্যে এসে পৌঁছেছি যে, এখান থেকে চন্দ্র-সূর্য কিছুই সহজে দেখা যাবার কথা নয়।
গরমের দিন হলেও, এ জায়গাটা বেশ ভিজে স্যাঁতসেঁতে, বোধ হয় অনেক নদী-নালা আছে বলে। নইলে শম্বরটাকে পায়ের দাগ দেখে ট্রাক করা সম্ভব হত না আমাদের পক্ষে।
এদিকটা ভিজে ভিজে হলেও, পশ্চিমের পাহাড়গুলোতে দাবানল লেগেছে। একটা বড় পাথরে বসে কফি খেতে খেতে, পাইপটাতে তামাক ভরতে ভরতে আমি সেই আগুনের মালার দিকে চেয়ে ছিলাম। ভারী চমৎকার লাগছিল এক পাহাড়ের গায়ে বসে, উপত্যকা-পেরুনো দূরের অন্য পাহাড়ের গায়ের আগুনের মালা দেখতে। ঐদিকে আগুন জ্বলাতে চারদিক দিয়ে গরম হাওয়া ছুটে আসছিল এদিকে।
হঠাৎ লক্ষ করলাম যে, জুডু কফি খাচ্ছে না, হাঁটু গেড়ে বসে সেই পশ্চিমের আগুনের দিকে চেয়ে কী সব মন্ত্র-টন্ত্র পড়ছে। ওকে দেখে মনে হচ্ছে যে, ও এ-জগতে নেই। ওর চোখের ভাব এমন হয়ে গেছে যে, মনে হচ্ছে ও আমাকে চেনে না।
ওর ঐসব প্রক্রিয়া শেষ করে জুডু আবারও আমাকে অনুনয়-বিনয় করে বলল, তোমার পায়ে পড়ি, এখনও পালিয়ে চলল।
আমি নিঃশব্দে ওকে পাশে রাখা আমার রাইফেলটিকে ইশারা করে দেখালাম।
ও চুপ করে গেল। রান্নার বন্দোবস্ত করতে লাগল। রান্না মানে চাল, ডাল আর তার সঙ্গে দু একটা আলু, পেঁয়াজ ও কাঁচালঙ্কা ছেড়ে সেদ্ধ করে নেওয়া।
খিচুড়িটা চাপানো হয়ে গেলে, পাইপটা ধরিয়ে, জুডুকে ডাকলাম আমি। ব্যাগ থেকে একটা বিড়ির বাণ্ডিল বের করে ওকে দিয়ে বললাম, এবার বল দেখি তুই, এই মউলির ব্যাপারটা কী? সব ভাল করে বল, খুলে বল।
জুডু একটা বিড়ি ধরিয়ে, পশ্চিমের দিকে পেছন ফিরে উবু হয়ে জানোয়ারের মতো বসে, বিড়বিড় করে বলতে লাগল।
জুডু উপজাতীয় মানুষ। ওরা খন্দ। ওদের মধ্যে অনেক সব বিশ্বাস, সংস্কার আছে; কিন্তু জুডুকে ভীতু আমি কখনোই বলতে পারব না। বরং বলব যে, আমার দীর্ঘ শিকারী জীবনে এমন সাহসী ও অভিজ্ঞ ট্র্যাকার আমি খুব কমই দেখেছি। ওর সাহস আমার চেয়ে কম তো নয়ই, বরং বেশিই।
তাই পাইপ টানতে টানতে জুডুর এই মউলি বৃত্তান্ত আমি খুব মনোযোগের সঙ্গে শুনতে লাগলাম।
জুডু চোখ বড় বড় করে, কিন্তু ফিসফিস করে বলছিল। যেন ওর কথা অন্য কেউ শুনে ফেলবে।
বলছিল– ঋজুবাবু, আমাদের অনেক দেবতা। টানা পেনু, ডারেনী পেনু, টাকেরী পেনু, খ্রিভি পেনু, কাটি পেনু, এসু পেনু, সারু পেনু।
টানা পেনু আর ডারেনী পেনু একই দেবী। তিনি হচ্ছেন গ্রামের দেবী। গ্রামকে বাঁচান। প্রতি গ্রামের পাশে এই দেবীর পাথরের ঠাঁই থাকে। ডারেনী পেনুর বন্ধু টাকেরী পেনু এবং ডারেনী পেনুর ভাই স্রিভি পেনু। স্রিভি পেনুর মারফতই যত পুজো, আরজি, আবদার করতে হয় আমাদের।
কিন্তু মউলি?
নামটা উচ্চারণ করেই জুড়ু একবার এদিক-ওদিক দেখে নিল, তারপর গলা আরও নামিয়ে বলল, মউলি জঙ্গলের দেবতা। আমরা তাকে বড় ভয় পাই। তাকে পুজো দেওয়া তো দূরের কথা, মউলি যেখানে থাকে আমরা তার ধার-কাছ পর্যন্ত মাড়াই না।
জুড়ু এই অবধি বলে, থেমে গিয়ে বলল, ঐ শম্বরটা আসলে শম্বর নয়। ওটা মউলির চর। আজ রাতেই মউলি আমাদের মারবে।
আমি বললাম, চুপ কর তো। তোর মতো সাহসী, জবরদস্তু শিকারী– তুইও কি না ভয় পাস? সঙ্গে রাইফেল নেই? তোর মউলি-ফউলি সকলের পেট ফাঁসিয়ে দেব হার্ড-নোজড় বুলেট মেরে।
জুডু ইলেকট্রিক শক্ খাওয়ার মতো চমকে উঠল। দু কানে দু হাত দিয়ে বলল, অমন বলতে নেই বাবু। পাপ হবে, পাপ হবে। ঐ রাইফেলটা সঙ্গে থেকেই যত বিপদ। আজ রাত কাটলে হয়!
আমি আবার ওকে আশ্বাস দিয়ে বললাম, তোর কোনও ভয় নেই, ভাল করে খিচুড়িটা রাঁধ দেখি, খিদে পেয়ে গেছে। আর আগুনটা জোর কর। অজানা-অচেনা জায়গা, হাতি থাকতে পারে, বাঘ থাকতে পারে, আগুনে আরও কাঠকুটো এনে ফেল যাতে সারা রাত আগুনটা জ্বলে। একেবারে অচেনা জায়গায় তাঁবু ফেলে নিশ্চিন্ত থাকা ঠিক নয়। হয়তো এর ধারেকাছেই জানোয়ার-চলা সঁড়িপথ থাকবে।
জুডুকে বললাম বটে আগুনটা জোর করতে, কিন্তু মনে হল না, ও এই তাঁবুর সামনে থেকে এক পা-ও নড়বে।
তাই পাইপের ছাই ঝেড়ে উঠে আমিই এদিক ওদিক গিয়ে শুকনো ডাল, খড়কুটো কুড়িয়ে আনতে গেলাম।
যখন নিচু হয়ে ওগুলো কুড়োচ্ছি, তখন হঠাৎ আমার মনে হল, আমার চারপাশে যেন কাদের সব ছায়া সরে সরে যাচ্ছে। কারা যেন ফিফিস্ করে কথা বলছে।
একটা ডাল কুড়িয়ে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ানো মাত্রই আমার মনে হল, আমি যেন আমার সামনের অন্ধকার থেকে সেই অন্ধকারতর অতিকায় শম্বরটাকে সরে যেতে দেখলাম। শম্বরটা সরে গেল, কিন্তু কোনও শব্দ হল না।
আমি স্তব্ধ হয়ে রইলাম এক মুহূর্ত।
পরক্ষণেই আমার হাসি পেল। নিজেকে মনে মনে আমি খুব বকলাম। লেখাপড়া শিখেছি, বিজ্ঞানের যুগে এসব কী যুক্তিহীন ভাবনা? তা ছাড়া, এরকম অচেনা পরিবেশে গভীর জঙ্গলে এই-ই তো আমার প্রথম রাত কাটানো নয়। ছোটবেলা থেকে আমি এই জীবনে অভ্যস্ত। এতে কোনও বাহাদুরি আছে বলে ভাবিনি কখনও। বরং চিরদিনই এই জীবনকে ভালবেসেছি। উপরে তারা-ভরা আকাশ, রাত-চরা পাখির ডাক, দূরের বনে বাঘের ডাক আর হরিণের টাউটাউ, এ সমস্ত তো চিরদিনই ঘুমপাড়ানী গানের মতোই মনে হয়েছে। এসবের মধ্যে কখনই কোনও ভয় বা অসঙ্গতি তো দেখিনি!
অথচ আজ কেন এমন হচ্ছে?
ফিরে এসে আগুনটা জোর করে দিয়ে পাথরটার উপরে বসে আমি পশ্চিমের পাহাড়গুলোর দিকে চেয়ে রইলাম। দাবানলের মালা পাহাড় দুটোকে যেন ঘিরে ফেলেছে। কী সুন্দর যে দেখাচ্ছে, তা বর্ণনা করার মতো ভাষা আমার নেই। নীচের খাদ থেকে একটা নাইট-জার পাখি সমানে ডেকে চলেছে– খাপু-খাপু-খাপু-খাপু-খাপু।
মাঝে-মাঝে বিরতি দিচ্ছে, আবার একটানা ডেকে চলেছে অনেকক্ষণ।
আগুনে ফুটফাট শব্দ করে কাঠ পুড়ছে। আগুনের ফুলঝুরি উঠছে। তারপর ফুলঝুরির মাথায় উঠে গিয়ে কাঠের কালো ছাইয়ের গুঁড়ো গোলমরিচের গুঁড়োর মতো নীচে এসে পড়ছে।
ঐদিকে তাকিয়ে বসে থাকতে-থাকতে হঠাৎই আমার খেয়াল হল যে, আজ চারিদিকের পাহাড় বনে একক নাইট-জারটার খাপু-খাপু-খাপু-খাপু আওয়াজ ছাড়া আর কোনও আওয়াজ নেই। আমাদের পাশেই তিরতির করে একটা ঝরনা বইছে, সেটা গিয়ে মিশেছে উপত্যকার নালায়, যেখানে ভাল জল আছে। এই গরমের দিনে সাধারণত এমন জায়গায় বসে থাকলে নীচের উপত্যকায় নানারকম জানোয়ারের চলাফেরার বিভিন্ন আওয়াজ শোনা যেত। হায়েনা হেঁকে উঠল হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ করে বুক কাঁপিয়ে। হয় উইয়ের ঢিবির কাছে, নয় মহুয়াতলায় ভাল্লুক নানারকম বিশ্রী আওয়াজ করে উই খেত বা মহুয়া খেত। আমলকীতলায় কোটরা হরিণের ব্রাক ব্বা ডাক শোনা যেত। অ্যালসেশিয়ান কুকুরের ডাকের মতো।
কিন্তু আজ রাতের সমস্ত প্রকৃতি যেন নিথর, নিস্তব্ধ। এমন কী, পেঁচার ডাক পর্যন্ত নেই। চতুর চিতার তাড়া-খাওয়া হনুমান দলের হু-হুঁ-হুঁ-হুঁপ ডাকে রাতের বনকে মুখরিত করা নেই। আজ কিছুই নেই।
বসে থাকতে-থাকতে হঠাৎ আমার মনে হল, আমি যে পাথরটায় বসেছিলাম, ঠিক তার পেছনে আমার গা-ঘেঁষে কে যেন এসে দাঁড়িয়েছে। কোনও মানুষ! আমি যেন আমার খাকি বুশ-শার্টের কলারের কাছে তার নিশ্বাসের আভাস পেলাম।
চমকে পেছন ফিরেই দেখি, না, কেউ নেই তো!
একটা একশো বছরের পুরোনো জংলী আমগাছ থেকে ঝুপ করে শুকনো পাতার উপর হাওয়ায় একটা আম ঝরে পড়ল। সেই নিস্তব্ধ রাতে সেই আওয়াজটুকুকেই যেন বোমা পড়ার আওয়াজ বলে মনে হল।
ওখানে বসে বসে আমি লক্ষ করছিলাম যে, জুডু রান্না করতে করতে মাঝে মাঝেই বাঁ হাত দিয়ে ওর গলার হাড়ের লকেটটাকে মুঠি করে ধরছিল।
আমি উৎসুক হয়ে শুধোলাম, ওটা কিসের হাড় রে জুডু?
জুডু আমার কথায় চমকে গিয়ে কেঁপে উঠল।
তারপর সামলে নিয়ে বলল, এটা অজগরের হাড়, মন্ত্ৰপড়া। আজ আমাকে বাঁচালে এই হাড়টাই বাঁচাবে মউলির হাত থেকে। আমার দিদিমা আমার ছোটবেলায় মন্ত্র পড়ে এই হাড়টা আমায় দিয়েছিল।
আমি হাড়টার দিকে অপলকে চেয়ে রইলাম। অজগরের হাড় আমি কখনই দেখিনি। আগুনের আলোকে সেই হাড়টা রঙ বদলাচ্ছে বলে মনে হল।
খাওয়া-দাওয়ার পর আমি আবার পাইপ ধরিয়ে বাইরে বসেছি পাথরটার উপর, এমন সময় জুডু যা কখনও করেনি তাই করল।
আমার কাছে এসে বলল, বাবু, আজ আমি কিন্তু তাঁবুর মধ্যে তোমার কাছে। শুয়ে থাকব।
আমি অবাক হলাম।
তারপর বললাম, তাই-ই শুস।
যাকে মানুষখেকো বাঘের জঙ্গলে কখনও গালাগালি করেও তাঁবুর মধ্যে শোয়াতে পারিনি, সে বরাবর বলেছে, আমার দম বন্ধ লাগে তাঁবুর মধ্যে সেই জুড়ু আজ স্বেচ্ছায় তাঁবুর মধ্যে শুতে চাইছে!
আমি পশ্চিমের পাহাড়গুলোর দিকে তাকিয়ে ছিলাম। জুডু আগুনের পাশেই বসে সেই তিরতিরে ঝরনায় আমাদের অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়িটা, এনামেলের থালা দুটো ও কফির কাপ দুটো ধুচ্ছিল।
এমন সময় হঠাৎ দেখলাম, যেন কোনও মন্ত্রবলে পশ্চিমের পাহাড়ের দাবানলগুলো সব একই সঙ্গে নিভে গেল। মনে হল, কে যেন পা দিয়ে মাড়িয়ে জঙ্গল-পোড়ানো শত সহস্র হস্ত প্রসারিত লেলিহান আগুনগুলোকে একসঙ্গে নিভিয়ে দিল।
আগুনগুলো নিভে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমের দিক থেকে একটা জোর ঝড়ের মতো হঠাৎ হাওয়া উঠল।
অথচ পূর্ব মুহূর্তে সব কিছু শান্ত ছিল।
হাওয়াটা জঙ্গলের গাছগাছালিতে ঝর ঝর করে সমুদ্রের আছড়ে-পড়া ঢেউয়ের মতো শব্দ করে আমাদের দিকে ধেয়ে এল। এত জোরে এল হাওয়াটা যে, তাঁবুটাকে প্রায় উড়িয়েই নিয়ে যাচ্ছিল। আমাকেও পাথর থেকে ফেলে দেওয়ার মতো জোর ছিল হাওয়াটার।
কিন্তু আশ্চর্য! হাওয়াটা আমাদের তাঁবু অতিক্রম করে গিয়েই একেবারে মরে গেল।
কী ব্যাপার বোঝার চেষ্টা করছি, এমন সময় নীচের উপত্যকা থেকে, ক্ষেতে লাঙ্গল দেওয়ার সময় চাষারা বলদের লেজ-মুচড়ে যেরকম সব অদ্ভুত ভাষা বলে, তেমন ভাষায় কারা যেন কথা বলতে লাগল। মনে হল, কারা যেন এই এক রাতে পুরো উপত্যকাটা চষে ফেলবে বলে ঠিক করেছে।
সেই আওয়াজটাও দু মিনিট পর একেবারে বন্ধ হয়ে গেল।
একটু পরে চাঁদ উঠল।
জুডু কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, বাবু, শুয়ে পড়ো। আজ আর বাইরে বেশি বসে কাজ নেই। চলো, শুয়ে পড়বে।
সত্যি কথা বলতে কী, আমার একটু যে ভয় করছিল না তা নয়। কিন্তু ভয়ের চেয়েও বড় কথা, পুরো জায়গাটা, এই রাতের বেলার জঙ্গলের অদ্ভুত শব্দ ও কাণ্ড দেখে আমার দারুণ এক ঔৎসুক্য জেগেছিল। ভূত-প্রেতে আমি কখনও বিশ্বাস করিনি। হাতে একটা রাইফেল থাকলে পৃথিবীর যে কোনও বিপদসঙ্কুল জায়গায় আমি হেঁটে যেতে পারি, রাতে ও দিনে। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত মানুষখেকো বাঘের থাবায় নিহত মানুষের অধভুক্ত শবের কাছেও কাটিয়েছি। একবার শুধু একটা মরামানুষের পা সটান সোজা হয়ে উঠেছিল। তখনও ভয় পাইনি, কারণ তারও একটা বুদ্ধিগ্রাহ্য কারণ ছিল। কিন্তু এমন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন আমি কখনও হইনি এর আগে। ঠিক কী ভাবে এই অনুভূতিকে গ্রহণ করব বুঝে উঠতে পারছিলাম না।
এই খন্দমালে আমার এই-ই প্রথম আসা নয়। আগেও বহুবার আমি এই অঞ্চলে এসেছি। খন্দুদের নিয়ে যতটুকু পড়াশুনা করা যায় করেছি। তাদের রীতি-নীতি দেব-দেবতা, সংস্কার-কুসংস্কার সম্বন্ধে আমি ওয়াকিবহাল।
কিন্তু জঙ্গল-জীবনের সমস্ত বিদ্যা, বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা দিয়ে এইসব কাণ্ডের কোনও ব্যাখ্যাতেই আমার পক্ষে পৌঁছনো সম্ভব হচ্ছিল না।
খন্দরা ওড়িশা ও অন্ধ্রপ্রদেশের সীমানার গঞ্জাম জেলার একটি জায়গায় বাস করত বহু-বহু বছর আগে। জায়গাটা ছিল খুব উঁচু-উঁচু পাহাড়শ্রেণী আর জঙ্গলে ঘেরা। জায়গাটার নাম ছিল শ্ৰাম্বুলি-ডিম্বলি। সেখান থেকে এসে এরা এইখানে বাসা বাঁধে অন্যদের তাড়া খেয়ে।
ওরা মনে করত যে, এইসব মাথা-উঁচু পাহাড়ের পরই পৃথিবী শেষ হয়ে গেছে। ওদের রাজ্য থেকে সামনে যতদূর চোখ যায়, ততদূর আদিগন্ত এমন গভীর জঙ্গলাবৃত পাহাড় ও জমি দেখা যেত যে, তাতে মানুষ কখনও বসবাস করতে পারে একথা কেউই ভাবেনি। ওদের মধ্যে একটা জনশ্রুতি আছে যে, যখন খা এইসব পাহাড়ে এসে উপস্থিত হয়েছিল, তখন তৎকালীন পাহাড়ী আদিবাসী কুমুরা তাদের সমস্ত জমি-জমা স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি খদের হাতে দিয়ে এইসব পাহাড়ের উপরের সমতল মালভূমি থেকে মেঘের ভেলায় চেপে চিরদিনের মতো অন্তর্ধান করেছিল।
খন্দরা মনে করত যে, পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা জামো পেনুর বড় ছেলের থেকে কুমুরা উদ্ভূত হয়েছে এবং খা উদ্ভূত হয়েছে জামো পেনুর সবচেয়ে ছোট ছেলের থেকে।
কিন্তু মউলি সম্বন্ধে আমি কখনও কিছু পড়িনি বা শুনিনি।
জুড়ু আবারও বলল, বাবু, শুয়ে পড়ো। বাইরে থেকো না আর।
তাঁবুর দৃপাশের পদা তোলা ছিল। গরমে এমন করেই আমরা শুই। জঙ্গলে গরমের দিনেও শেষ রাতে ভারী হিম পড়ে। তাই মাথার উপর তাঁবু থাকলেই যথেষ্ট। প্রথম রাতে গরম লাগে, তাই যাতে হাওয়া চলাচল করতে পারে তার জন্যে পদা খোলা থাকে।
তাঁবুর মধ্যে ঢুকেই জুডু বলল, বাবু, আজ পদা খুলে শুয়ো না। ওকে আমি ধমকে বললাম, চুপ কর তো তুই। গরমে কি মারা যাব নাকি?
তারপর প্রসঙ্গ বদলাবার জন্যে বললাম, শম্বরটা কোনদিকে গেছে বল তো? আমার মনে হয়, ও ধারেকাছেই আছে। হয় নীচের নালার পাশে, নয়তো সামনের মালভূমির উপরে। কাল ভোরেই ওর সঙ্গে আমাদের মোলাকাত হবে।
জুডু তাঁবুর মধ্যে হাঁটু গেড়ে বসে সেই অজগরের হাড়টা ছুঁয়ে কী সব বিড়বিড় করে বলল। একটা আশ্চর্য হাসি ফুটে উঠল ওর মুখে। ও বলল, বাবু, তুমি বিশ্বাস করছ না.যে ওটা শম্বর নয়? অতবড় শম্বর যে হয় না এ কথা আমার ও তোমার দুজনেরই বোঝা উচিত ছিল। তোমাকে বলছি আমি যে ওটা মউলির চর।
আমি যত না জুডুকে সাহস দেবার জন্যে বললাম, তার চেয়েও বেশি নিজেকে সাহস যোগাবার জন্যে আবারও বললাম, তোর মউলির নিকুচি করেছি।
বলেই, রাইফেলের বোল্ট খুলে, আরও দুটি গুলি ভরে নিয়ে ম্যাগাজিনে পাঁচটা ও ব্যারেলে একটা রেখে, সেফটি ক্যাচটা দেখে নিয়ে জুতোটা খুলে ফেলে স্লিপিং ব্যাগের উপরে শুয়ে পড়লাম।
জুডু আমার পাশ ঘেঁষে শুলো।
সারাদিনে প্রায় দশ-বারো মাইল হাঁটা হয়েছে চড়াইয়ে-উৎরাইয়ে, বেশির ভাগই জানোয়ার-চলা সঁড়িপথ দিয়ে। পথ বলতে এখানে কিছুই নেই। তারপর পেটে খাবার পড়েছে। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছিল।
বাইরে এখন কোনও শব্দ নেই। শব্দহীন জগতে জঙ্গল-পাহাড় উদ্ভাসিত করে চাঁদ উঠেছে। তাঁবুর পদার ফাঁক দিয়ে চাঁদের আলো এসে লুটিয়ে পড়েছে। নীচের উপত্যকার সাদা-সাদা পত্রশূন্য গেণ্ডলী গাছগুলোর ডালগুলোতে চাঁদের আলো পড়ে চকচক করছে।
মাঝে-মাঝে এই নিস্তব্ধ শব্দহীন পরিবেশকে চমকে দিয়ে একলা রাত-জাগা নাইট-জার পাখিটা খাপু-খাপু-খাপু-খাপু করে ডেকে উঠছে শুধু।
কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না।
হঠাৎ জোর ঝড়ের মতো হাওয়ার শব্দে আমার ঘুম ভেঙে গেল।
চোখ খুলেই, জঙ্গলে অস্বস্তি লাগলে যে-কোনও শিকারী যা করে, আমি তাই-ই করলাম। ডান হাতটা বাড়িয়ে দিলাম, তাঁবুর গায়ে হেলান দিয়ে যেখানে লোডেড রাইফেলটা রেখেছিলাম সেদিকে।
কিন্তু রাইফেলটা পেলাম না।
ধড়মড়িয়ে উঠে বসে দেখি রাইফেলটা লোপাট।
জুডুও নেই।
কোথায় গেল জুডু?
বাইরে তাকিয়ে দেখি, চাঁদ ডুবে গেছে পাহাড়ের আড়ালে। আর সেই অন্ধকারে শুধু সবুজ তারাগুলো নরম আলো ছড়াচ্ছে গ্রীষ্মের বাদামী জঙ্গলের উপর।
বালিশের তলা থেকে টর্চটা বের করে তাঁবুর বাইরে বেরোলাম। টর্চ জ্বেলে এদিক-ওদিক দেখলাম। বার বার ডাকলাম, জুড়ু, জুড়ু, জুডু।
সেই ঝড়ের মতো হাওয়াটা শুকনো ফুলের মতো আমার ডাককে উড়িয়ে নিয়ে গেল। পাহাড়ে-পাহাড়ে যেন চতুর্দিক থেকে ডাক উঠল। জুড়ু-জুড়ু-জুডু।
কিন্তু জুডুকে কোথাও দেখা গেল না। তাঁবুর ভিতরে ফেরার চেষ্টা করলাম। আমার টর্চের আলোয় তাঁবুর মধ্যে কী একটা সাদা জিনিস পড়ে থাকতে দেখলাম। কাছে গিয়ে দেখি জুডুর গলার সেই অজগরের হাড়টা।
কে যেন আমাকে বলল, হাড়টা কুড়িয়ে নাও। এক্ষুনি কুড়িয়ে নাও হাড়টা।
আমি দৌড়ে গিয়ে হাড়টা কুড়িয়ে নিয়ে আমার বুক-পকেটে রাখলাম।
ততক্ষণে হাওয়াটা এত জোর হয়েছে যে, তাঁবুর মধ্যে থাকাটা নিরাপদ বলে মনে হল না আমার। যে-কোনও মুহূর্তে তাঁবু চাপা পড়তে হতে পারে।
আমি তাড়াতাড়ি বাইরে এসে সেই পাথরটার উপরে বসলাম। নিজেকে স্বাভাবিক করার জন্যে পাইপটা ধরাবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু ঐ হাওয়াতে কিছুতেই দেশলাই জ্বলল না।
কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই হাওয়ার তোড়ে তাঁবুটাকে উল্টে ফেলল। অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়িটা হাওয়ার তোড়ে গড়িয়ে গিয়ে একটা পাথরে গিয়ে ধাক্কা খেল। টং করে আওয়াজ হল।
ধাতব আওয়াজটা শুনে ভাল লাগল। এটার মধ্যে অন্তত কোনও অস্বাভাবিকতা নেই।
হাওয়াটা যত জোর হতে লাগল, আমার মনে হতে লাগল নীচের উপত্যকা থেকে সবগুলো গাছ মাটি ছেড়ে উঠে আমার দিকেই এগিয়ে আসছে। পিছনে তাকিয়ে দেখি, পাহাড়ের গা থেকেও যেন গাছগুলো নেমে আমার দিকে হেঁটে আসছে। তাদের যেন পা গজিয়েছে। হাওয়াতে ডালপালাগুলো এমন আন্দোলিত হচ্ছিল যে, আমার মনে হল ওরা যেন ওদের হাত নেড়ে নেড়ে আমাকে ভয় দেখাচ্ছে।
জঙ্গলে কখনও রাইফেল-বন্দুক ছাড়া থাকিনি। নিদেনপক্ষে কোমরে পিস্তলটা গোঁজা থাকেই। অস্ত্র থাকলেও করার আমার কিছুই ছিল না, কিন্তু তবুও হয়তো এতটা অসহায়, নিরাশ্রয় লাগত না নিজেকে।
ভয়ে আমার কপাল ঘেমে উঠল।
আর একবার জুডুকে ডাকবার চেষ্টা করলাম।
কিন্তু আমার গলা দিয়ে আওয়াজ বার হল না।
হঠাৎ দেখলাম, দক্ষিণ দিকে গাছের গুঁড়িতে আটকে থাকা ভুলুণ্ঠিত তাঁবুটার ঠিক সামনে সেই শম্বরটা দাঁড়িয়ে আছে, আর তার পিঠের উপরে ভীষণ লম্বা রোগা একজন ঝাঁকড়া চুলওয়ালা নগ্ন লোক বসে আছে।
হঠাৎ আমার চতুর্দিকে গাছেদের সঙ্গে সঙ্গে যেন নানা জানোয়ারও আমাকে ঘিরে ফেলতে লাগল। শম্বর, হরিণ, কোরা, নীলগাই, শুয়োর, শজারু–যেসব জানোয়ার আমি ছোটবেলা থেকে সহজে শিকার করেছি। আমার মনে হল, ঐ মহীরুহগুলো আর জানোয়ারগুলো সবাই মিলে আমাকে পায়ে মাড়িয়ে আজ পিষে ফেলবে।
আমি দাঁড়িয়ে উঠে বলবার চেষ্টা করলাম, আর করব না। আর শিকার করব না। আমাকে ক্ষমা করো।
কিন্তু আমার গলা দিয়ে কোনও আওয়াজ বের হল না।
আমি পেছন ফিরে দৌড়ে পালাতে গেলাম। কিন্তু আমার চারিদিকে ঐ শম্বরটা ঐ লোকটাকে পিঠে নিয়ে ঘুরতে লাগল। আমার পালাবার পথ বন্ধ করে দিল। আমি পাগলের মতো এদিক ওদিক দৌড়তে লাগলাম। পাথরে হোঁচট খেয়ে পড়ে যেতে লাগলাম বারে বারে।
ভয়ে আমার গলা শুকিয়ে এল। আমি কাঁদতে গেলাম, কিন্তু আমার গলা দিয়ে তবু স্বর বেরোল না।
আমি আরকেবার উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু পারলাম না, পড়ে গেলাম।
তারপর আর কিছু মনে নেই আমার।
অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার আগে আমার চোখের সামনে সেই প্রাগৈতিহাসিক ধূসর-রঙা জটাজুট-সম্বলিত শম্বরটার বড় বড় সবুজ চোখ দুটো জ্বলজ্বল করতে লাগল।
.
০২.
কে যেন আমার নাম ধরে ডাকছিল।
যেন অনেক দূর থেকে ডাকছিল, যেন স্বপ্নের মধ্যে ডাকছিল। যেন আমার মা ছোটবেলা স্কুল থেকে ফেরার পর আমার খাবার দিয়ে আমাকে ডাকছিলেন।
কে যেন বড় আদর করে, আনন্দে আমাকে ডাকছিল।
আস্তে আস্তে আমি চোখ খুললাম।
দেখি, আমার মুখের দিকে ঝুঁকে তিন-চারজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। প্রবল জ্বরে যেমন ঘোর থাকে, তেমনই ঘোরে ছিলাম আমি।
চোখ খুলতে আমার ভারী কষ্ট হল।
অনেক কষ্টে চোখ খুলতেই রোদে আমার চোখ ঝলসে গেল। কে যেন আমার মাথাটাকে তুলে ধরে নিজের কোলে নিয়ে বসল।
আবার আমি তাকালাম, এবার দেখলাম, আমার মাথাটাকে কোলে নিয়ে বসে জুডু আমার মুখের উপর মুখ ঝুঁকিয়ে বসে আছে।
ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম, আমার দুই বন্ধু জর্জ আর কোন্ আমার দুপাশে বসে আছে।
জর্জ বলল, হাই ঋজু! হাউ ডু ইউ ফিল?
জর্জ মাটিতে পড়ে-থাকা আমার পাইপটা তুলে নিয়ে নিজের টোব্যাকো-পাউচ থেকে বের করে থ্রী-নান টোব্যাকো ভরে দিতে লাগল।
আমি উঠে বসলাম।
আমার কফি খাওয়া শেষ হলে, জর্জ পাইপটা ধরিয়ে দিল ওর লাইটার দিয়ে।
ওরা দুজনে হাসছিল।
কেন হাসতে হাসতে আমাকে বলল, হোয়াট ডিড ইউ সী লাস্ট নাইট। ঘোসট?
আমি উত্তর দেবার আগেই জর্জ হাসতে হাসতে বলল, মাই ফুট।
আমি উত্তর দিলাম না।
শুধু জর্জ বা কে বলে কথা নেই, আমার সভ্য শিক্ষিত, শহুরে বন্ধুদের কেউই যে আমার কথা বিশ্বাস করবে না, তা আমি বুঝতে পারছিলাম।
কফি খেয়ে আস্তে আস্তে উঠে পড়লাম। মাথাটা ভার। চোখে ব্যথা।
জর্জ বলল, ইউ আর এ সীলি গোট। কেন্ শট আ টাইগার দিস্ মর্নিং ইন দি ফারস্ট বীট। অ্যান্ড ইউ কে হিয়ার টু শুট আ ঘোস্ট!
জুডু ইংরেজী বোঝে না।
ও মালপত্র কাঁধে তুলে নিয়ে রওয়ানা হবার জন্যে তৈরি হল।
জর্জ আর কেন আগে-আগে হাঁটতে লাগল।
জুডু ফিসফিস করে বলল, বাবু, আমাকে মাপ করো, আমি না পালিয়ে পারিনি। আমার কিছু হত না। অজগরের মন্ত্রপড়া হাড় শুধু আমার কাছেই ছিল। তুমি আমার কথা শুনলে না– তাই তোমাকে ওটা দিয়ে আমি পালাতে বাধ্য হলাম।
জর্জ পিছন ফিরে শুধোলো, আর য়ু ডিসকাসিং বাউট দ্য ফিচারস্ অফ দ্য ঘোষ্ট? ইউ সিলি কাওয়ার্ড!
আমি জবাব দিলাম না।
যেই ওরা আবার অন্যদিকে মুখ ফেরাল, আমি তাড়াতাড়ি বুক-পকেটে হাত ঢুকিয়ে অজগরের হাড়টাকে জুডুর হাতের মুঠোয় লুকিয়ে দিয়ে দিলাম।
কে বলল, ইউ হ্যাভ সীন সাম পি-ফাউলস্ অন আওয়ার ওয়ে আপ হিয়ার। লেটুস শুট আ কাপ। জর্জ হ্যাঁজ হিজ শটগান উইথ হিম।
আমি বললাম, আই অ্যাম গোয়িং টু গিভ আ শুটিং ফর গুড়। জর্জ আর কেন্ দুজনে একই সঙ্গে কল্ক করে হেসে উঠল। বলল, ওঃ ডিয়ার; ডিয়ার। দ্যাটস্ দ্য জোক অফ দ্য ইয়ার।
আমি আর জুডু পাশাপাশি হেঁটে চললাম। আমার বন্ধুদের কথার কোনও জবাব দিলাম না। কারণ, জবাব দিয়ে লাভ ছিল না কোনও।
.
তিনকড়ি
পর পর পাঁচ ভাই মারা যাওয়ার পর যখন কড়িদা জন্মাল, তখন কড়িদার মা তাঁর নাম রাখলেন তিনকড়ি। ঠিক যে নাম রাখলেন তা নয়, তিন কড়ি দিয়ে কড়িদার কাকিমা কিনে নিলেন তাকে তার মার কাছ থেকে।
সকলের ভয় ছিল যে, কড়িদাও বুঝি বাঁচবে না। কিন্তু কড়িদা শেষ পর্যন্ত বেঁচে গেল।
কড়িদাকে আমি প্রথম দেখি যখন আমি কলেজে ঢুকেছি তখন। আমার পিসীমার বাড়ি ছিল আসামের ধুবড়ি শহর থেকে কচুগাঁওয়ের দিকে যাবার রাস্তায় তামাহাট বলে ছোট একটা গঞ্জে। কড়িদারা থাকত তামাহাটের আগে কুমারগঞ্জ বলে আরেকটা গ্রামে।
কড়িদা যখন ছোট তখনই কড়িদার বাবা মারা যান। বিধবা মা তাঁর অন্তরের সমস্ত ঐশ্বর্য ও সিন্দুকের যৎসামান্য পুঁজি দিয়ে কড়িদাকে মানুষ করেন। কিন্তু তিনি কখনও নিজের ছেলেকে নিজের ছেলে মনে করার মতো সাহসী হয়ে উঠতে পারেননি। পারেননি এই ভয়ে যে, পাছে তাঁর অন্য পাঁচ ছেলের মতোই কড়িদাও পালিয়ে যায়।
পিসীমা ও পিসেমশাই কড়িদাকে নিজেদের ছেলেদের সঙ্গে একইরকম করে বড় করতে থাকেন। এখানে ওখানে হস্টেলে থেকে পড়াশুনা করত কড়িদা আমার অন্য দুই প্রায়-সমবয়সী পিসতুতো ভাইয়ের সঙ্গে। তাই কলকাতায় থাকতাম বলে তাদের কারও সঙ্গে আমার বড় একটা দেখা হত না।
কলেজের গরমের ছুটিতে ধুবড়ি গেলাম। রাত কাটালাম কড়িদার কাকা পূর্ণকাকার বাড়িতে। আজকে আমার পিসেমশাই বা পূর্ণকাকা কেউ আর বেঁচে নেই।
বাড়িতে বিজলীর আলো ছিল না। পাখাও ছিল না। সে রাতে বড় ভ্যাপসা গুমোট গরম ছিল। ব্রহ্মপুত্রর দিক থেকে হাওয়াও আসছিল না একটুও। এদিকে প্রচণ্ড মশা। বাধ্য হয়ে মশারি টানিয়ে শুতে হয়েছিল। কড়িদার খুড়তুতো দিদি ভারতীদি যত্ন করে মশারি টানিয়ে দিয়ে গেছিলেন। কড়িদা আর আমি পাশাপাশি খাটে শুয়েছিলাম। আমাকে জানলার পাশের খাটে যেখানে হাওয়া লাগার সম্ভাবনা বেশি, সেখানে শুতে দিয়েছিল কড়িদা।
আমি আজন্ম কলকাতায় মানুষ, বৈদ্যুতিক পাখার হাওয়ায় অভ্যস্ত; সাহেবী কলেজে পড়ি, সমস্ত মিলিয়ে সেই পাখাহীন ঘরে, মশারির দুর্গের মধ্যে বন্দী হয়ে একজন গ্রাম্য ছেলের পাশে শুয়ে, যাকে আমি সেদিনই প্রথম দেখলাম বলতে গেলে, আমার ভারী অস্বস্তি লাগছিল। কড়িদার সঙ্গে গল্প যে কী করব তার বিষয়ও খুঁজে পাচ্ছিলাম না। কলকাতার সেই-আমির সঙ্গে ছোট-ছোট অনগ্রসর জায়গায় স্কুলের হস্টেলে-মানুষ গেঁয়ো ছেলেটির সঙ্গে ভাব হচ্ছিল না।
কড়িদা তখন পর্যন্ত আমার সঙ্গে বিশেষ কথা বলেনি। হাসি-হাসি মুখে আমার দিকে চেয়ে দু-একটা কথা বলেছিল মাত্র। তবে সেই মুখের দিকে প্রথমবার চেয়েই আমার মনে হয়েছিল যে, এমন নিষ্পাপ, স্বর্গীয় মুখ আমি আগে কখনও দেখিনি।
রাত গম্ভীর হচ্ছিল। মশারির মধ্য গরম এবং বাইরে মশার পিপিনানি বেড়েই চলছিল। ঘরের পাশে একটা কী-যেন ফুলের ঝোঁপ ছিল। সেই ঝোঁপ থেকে ঝিম-ধরা গরমের মতো একটা ঝিম-ধরা গন্ধের ঝাঁজ উঠছিল।
আমার কিছুতেই ঘুম আসছিল না। কিন্তু কড়িদার যে কেন ঘুম আসছিল না, তা বুঝতে পারছিলাম না। এটাই তার ঘর, এই ঘরেই সে রোজ শোয়, বৈদ্যুতিক পাখাতে সে অভ্যস্তও নয়। তাহলে?
ছটফট করতে করতে বোধহয় চোখ জুড়ে এসেছিল এক সময়। চোখ জুড়ে আসার পরই বেশ একটা হালকা হাওয়া আসতে লাগল মাথার দিক থেকে। আধ-ঘুমন্ত অবস্থায় ভাবলাম, বোধহয় নদীর দিক থেকে হাওয়া দিল।
পাশের বাড়ির কতগুলো রাজহাঁসের প্যাকপ্যাঁক আওয়াজে ভোরবেলা ঘুম ভেঙে গেল। বিছানায় উঠে বসে দেখি কড়িদা খাটের মাথার দিকে একটা চেয়ারে বসে ঘুমিয়ে পড়েছে। অসহায় ভঙ্গিমায় তার শরীরটা চেয়ারের উপরে ছড়িয়ে আছে। পায়ের কাছে হাত-পাখাটা মাটিতে পড়ে আছে।
কড়িদা কখন ঘুমিয়েছে জানি না; হয়তো বা সারারাত আমাকে হাওয়া করে এই একটু আগেই। মশার কামড়ে হাত দুটো লাল চাকা-চাকা হয়ে ফুলে গেছে। কিন্তু মুখে সেই অম্লান অনুযোগহীন অভিযোগহীন হাসি।
এই কড়িদা!
যাকে সে জানে না ভাল করে, চেনে না, যার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা নেই, বন্ধুত্ব নেই, যার সঙ্গে নেই কোনও দেনা-পাওনার সম্পর্ক, সেই কলকাতার ছেলেটাকে নিজে সারারাত মশার কামড় খেয়ে হাতপাখা চালিয়ে ঘুম পাড়ানোর অযাচিত সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন ভার একমাত্র কড়িদাই নিতে পারত।
সকলের প্রতিই ঠিক একই রকম ব্যবহার ছিল তার। তামাহাটে পৌঁছে খুব মজা করতাম আমরা। পূর্ণকাকার দোনলা বন্দুক নিয়ে পাহাড়ে বনে ঘুরে বেড়াতাম।
সাত-বোশেখীর মেলা বসেছিল রাঙামাটি পাহাড়ে। টুঙ-বাগানের ছায়া-শীতল ভয়-ভয় সাপ-সাপ বাঘ-বাঘ গন্ধভরা বুনো পথ মাড়িয়ে রাঙামাটি-পর্বতজুয়ারের জঙ্গল। ম্যাচ-সর্দারদের বাসা সেখানে। সারা দুপুর নিকোনো দাওয়ায় বসে তেল-চুকচুক সটান চুলে কাঠের কাঁকই খুঁজে, তাঁত বোনে সেখানে ম্যাচ-মেয়েরা। আর হলুদ-লাল কাঁঠাল পাতা ঝরে পাহাড়ী হাওয়ায় টুপ-টাপ, খুস্স্-খাস্ করে। সেখানে নিয়ে গেল কড়িদা আমায়। ম্যাচ-সর্দার লম্বা বিড়ি মুখে দিয়ে বাইরে এসে দা দিয়ে একটা কাঠ কেটে কেটে কী যেন বানাচ্ছিল।
কড়িদা বলল, আছে কেমন?
বুড়ো সর্দার ঘোলাটে চোখ তুলে বলল, ভাল আছি।
কড়িদা হাসল; বলল, তুমি তো ভাল থাকবেই। সে আছে কেমন?
সর্দার এবার অবাক হল।
বড় বড় বিস্মিত চোখ তুলে, নিজের বাতে-ধরা শরীরটাকে কোনওক্রমে ওঠাল, হাড়ে হাড়ে কটাকট শব্দ তুলে, তারপর দাওয়ার এক কোনায় একটা বাঁশের চালায় নিয়ে গেল আমাদের।
দেখি, একটা বাদামী রঙা ভুটিয়া কুকুর খড়ের উপর শুয়ে আছে। তার ঘাড়ের কাছে অনেকখানি দগদগে ঘা। কী-সব পাতা-টাতা বেটে লাগানো আছে। তাতে। ঘরময় ঘিনঘিন করে মাছি উড়ছে।
কড়িদা বিড়বিড় করে বলল, নাঃ, অবস্থা ভাল নয়। ধুবড়ি গিয়ে ওষুধ আনতে হবে।
আমি শুধোলাম, কী হয়েছিল?
কড়িদা বলল, সাতদিন আগে ওকে একটা ছোট চিতা কামড়ে দিয়েছিল।
তুমি জানলে কী করে?
এই সর্দার হাটে এসেছিল পরশুদিন, ওর মুখে শুনেছিলাম।
কুকুরটা বুঝি তোমার খুব প্রিয়?
কড়িদা অবাক চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থাকল। কী যেন ভাবল অল্পক্ষণ।
তারপর হেসে বলল, হ্যাঁ! খুব প্রিয়।
কী নাম কুকুরটার?
কড়িদা বলল, জানি না তো।
সর্দার বলল, ডালু।
তারপর সর্দারই বলল, দিন দশ হল আমার বেয়াই কচুগাঁও থেকে আমার জন্যে জামাইয়ের সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়েছে।
আমি আরও অবাক হলাম সে-কথা শুনে।
কড়িদা বলল, কুকুরটাকে আগে দেখিনি। তবে বেচারীকে চিতাবাঘে কামড়েছে শুনে বড় কষ্ট হয়েছিল। তা ছাড়া বুড়োর মুখ দেখে মনে হয়েছিল, কুকুরটাকে বুড়ো বড় ভালবেসে ফেলেছে। আর বুড়োর খুব ভাল লাগবে যদি আমি আসি, তাই তোমাকে নিয়ে চলে এলাম।
আমি বললাম, এই জন্যে সাইকেলে ও হেঁটে বারো মাইল এলে তুমি? মিছিমিছি? বুড়ো কি তোমাকে পাটের ব্যবসায় সাহায্য করে?
কড়িদা আবার অনেকক্ষণ চেয়ে থাকল আমার দিকে। বলল, না তো! বুড়োর সঙ্গে হাটে দেখা হয় মাঝে মাঝে।
কড়িদা পকেট থেকে পটাশ-পারমাঙানেটের লাল লাল কুচি বের করল, কাগজে মোড়া। বুড়োকে বলল, গরম জলে এই ওষুধ একটু গুলে ঘা-টাকে ভাল করে ধোবে বারবার। কাল আমি আবার আসব ওষুধ নিয়ে।
পর্বতজুয়ার থেকে অনেকখানি হেঁটে এসে তারপর সাইকেলে ফিরছিলাম আমরা। মাইল তিনেক রাস্তা চষা-ক্ষেতের আলের উপর দিয়ে সাইকেল চালাতে হয়। পেছনের হাড়গোড় প্রায় ভেঙে যাওয়ার উপক্রম হল আমার।
রেগেমেগে কড়িদাকে বললাম, কোনও মানে হয়? একজন প্রায় অচেনা-অজানা লোকের জন্যে আর তার একটা সাধারণ কুকুরের জন্যে এই হয়রানির?
কড়িদা হাসল। সাইকেল চালাতে চালাতে বলল, একটু জিরিয়ে নাও। এসো, ওই বড় গাছটার নীচে বসি একটুক্ষণ।
সাইকেল দুটো গাছে ঠেস দিয়ে রেখে আমরা মুখোমুখি বসলাম। পশ্চিমের আকাশে সবে সন্ধ্যাতারা উঠেছে। ভারী একটা শান্তির পরিবেশ চারিদিকে। সন্ধে হবার ঠিক আগে নিরিবিলি জায়গায় থাকলে বুকের মধ্যেটা যেন কেমন করে ওঠে।
কড়িদা বলল, তুমি বোধহয় লক্ষ করোনি ম্যাচ-সর্দার যখন হাসল, তখন তার মুখটা কেমন দেখাচ্ছিল। তুমি কি কুকুরটার চোখের দিকে তাকিয়েছিলে? তাকাওনি তো? তোমার দোষ নেই। কেউই তাকায় না। কিন্তু তাকালে বুঝতে পারতে, কুকুরটাও কত খুশি হয়েছিল আমাদের দেখে।
তারপর আবার ও হাসতে হাসতে হঠাৎ বলল, জানি, তোমার খুব কষ্ট হল। ঠিক আছে। কাল আমি একাই আসব। ওষুধ আনতে হবে সকালে গিয়ে। ঘায়ের অবস্থা ভাল না কুকুরটার।
আমি বিরক্ত গলায় বললাম, কলকাতার পথে-ঘাটে এমন কত কুকুর তো রোজ মরে। বড়লোকদের শৌখিন কুকুর ছাড়া কুকুরের চিকিৎসার কথা তো কখনও শুনিনি। কুকুরটা মরে গেলে তোমার কী যাবে-আসবে?
কড়িদার মুখটা এক মুহূর্তের জন্যে গম্ভীর হয়ে গেল। তার পরেই আবার সেই আশ্চর্য, উদার অনাবিল হাসিতে ভরে গেল। ডান হাতে এক মুঠো দুর্বাঘাস ছিঁড়ে বলল, দ্যাখো, কেউ মরে গেলে কারও কিছু এসে যায় না। আমাদের মতো সাধারণ লোক, কুকুর-মুকুর এইসব। কিন্তু…
কিন্তু…বলেই কড়িদা থেমে গেল।
আর কিছুই বলল না।
পরে বলল, তোমার মতো ভাষা আমার নেই, ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারব না। কিন্তু অন্য কাউকে খুশি দেখলে, সুখী দেখলে আমার খুব ভাল লাগে। কী যে ভাল লাগে তা তোমাকে বুঝিয়ে বলতে পারব না। সে যেই-ই হোক না কেন। আর, কাউকে দুঃখী দেখলে আমার বুকের মধ্যে বড় কষ্ট হয়।
আমি গেঁয়ো মানুষ; আমি অমনিই। আমাকে কেউ বোঝে না।
.
এরপর কড়িদা কর্মজীবনে কলকাতায় এসেছিল। আমার চেয়ে বয়সে দু বছরের মাত্র বড় ছিল। সেই গেঁয়ো নোকটা শহরে এসেও একটুও বদলাল না। কলকাতার কেজো জগতের সমস্ত স্বার্থপর লোকই তাকে পুরোপুরি পেয়ে বসেছিল। যার যা অসুবিধা, ডাকো কড়িকে। ডাক না-পাঠালেই বা কী, অসুবিধার কথা জানতে পারলেই হল, কড়িদা ঠিক সেখানে গিয়ে পৌঁছত। নিজের কাজকর্ম করে এবং রীতিমত ক্লান্ত থাকার পরেও যে কড়িদা কী করে এত লোকের জন্যে এত কিছু করত তা ভাবতেও অবাক লাগে।
কেউ যদি কখনও কড়িদার ছোট্ট বাড়িতে গিয়ে পৌঁছত, তাহলে তার যে কী আনন্দ হত তা তার মুখের হাসি যে না দেখেছে, সে বুঝবে না।
কড়িদা বলত, বুঝলে, আমরা হচ্ছি সাধারণ লোক, আমাদের উপর কোনও দায়-টায় নেই, কোনও বড় কাজ আমাদের দ্বারা হবে না, আমরা মরে গেলে কারও কিছু যাবে-আসবে না, ময়দানে স্ট্যাচু বানাবে না কেউ, এই রকম হেসে-খেলে বেঁচে থাকলেই খুশি।
হেসে-খেলেই থাকত কড়িদা। নিজের যে কোনওরকম অসুবিধে ছিল, দুঃখ ছিল মানসিক, কষ্ট ছিল শারীরিক, তা কেউ কখনও জানতে পারেনি। সমস্তক্ষণ সে অন্যের কষ্ট লাঘব করার জন্যেই এমন ব্যস্ত থাকত যে, নিজের দিকে তাকাবার অবকাশ পায়নি কখনও। অন্যের জন্যে, অন্যের কারণে নিজেকে ডুবিয়ে রাখার স্বর্গীয় সুখের আস্বাদ সে পেয়েছিল, আর সেই সুখেই ঝুঁদ হয়ে থাকত।
শুনলাম, কড়িদার পেটে নাকি ব্যথা হয়। শরীরে কী সব গোলমাল। চেহারা ও হাসি দেখে কিছু বোঝার উপায় ছিল না কারও।
হঠাৎ শুনলাম, কড়িদা হাসপাতালে ভর্তি হবে। কী সব পরীক্ষা-টরীক্ষা হবে–সিস্টোগ্রাফ-বায়োপসি ইত্যাদি বায়োপসি করে ধরা পড়ল ক্যান্সার।
যেদিন অপারেশন, তার আগের দিন নার্সিং হোমে তাকে দেখতে গেলাম।
আমি যেতেই কড়িদা উঠে বসল, জমিয়ে গল্প জুড়ে দিল, যেন ওটাও তার বাড়ির বৈঠকখানা। চমৎকার দেখাচ্ছিল কড়িদাকে। ধুতি আর পাতলা লংক্লথের পাঞ্জাবিতে।
আমি যখন উঠলাম, বলল, শরীরের যত্ন নিও, তুমি বড় বেশি খাটো, অত্যাচার করো বড়।
পরদিন অপারেশন হল। আর জ্ঞান ফিরল না। কড়িদা হাসতে হাসতেই বলতে গেলে, অত বড় দুরারোগ্য রোগটাকে হারিয়ে দিয়ে, আমাদের মতো যাটো মাপের সব মানুষদের মাথা ছাড়িয়ে তার যেখানে জায়গা সেখানে চলে গেল!
প্রায়ই মনে পড়ে, এবং চিরদিন পড়বে যে, কড়িদা একদিন সন্ধ্যাতারাকে সাক্ষী রেখে বলেছিল, কেউ মরে গেলে কারও কিছু আসে যায় না। কিন্তু…
আজ আমি জানি, তুমি সেদিন ঠিক বলোনি কড়িদা। কেউ কেউ মরে গেলে কারও কারও যায়-আসে নিশ্চয়ই, বড় বেশি যায়-আসে।
কড়িদার মা এখনও বেঁচে আছেন। আমার পিসীমা বড় সস্ত দামে কড়িদাকে কিনেছিলেন। মাত্র তিনটি কড়ি দিয়ে!
কিন্তু পৃথিবীর সব কড়ি দিয়েও কি তোমার দাম দেওয়া যেত কড়িদা?
.
টেনাগড়ে টেনশন
খগা সরকার আর ভগা সরকারকে চিনত না এমন লোক টেনাগড়ে কেউ ছিল না। পাহাড়-জঙ্গলে ঘেরা ছোট্ট শহর এই টেনাগড়। এখানে সকলেই সকলকে চেনে।
খগাদার বয়স হয়েছে ষাট-টাট। শৌখিন লোক। যৌবনে বেহালা বাজাতেন, শিকার করতেন, ওকালতিও। পিতৃপুরুষের বহু সম্পত্তি ছিল বিহারের নানা জায়গায়। তাই “খেটে খেয়ে তিনি জনগণের সামিল হতে চাননি। কিন্তু প্রয়োজন না থাকলেও খাটতে তিনি ভালবাসতেন এবং পরিশ্রমে বিশ্বাস করতেন।
খগাদার ভাই ভগাদার বয়স তিরিশ-টিরিশ হবে। টেনাগড়ে তিনি প্রায়ই নানা ধরনের খবরের সৃষ্টি করে থাকেন। লোকটি ভাল।
খগাদা এখন রিটায়ার্ড। ইদানীং চটের উপরে গুনছুঁচে রঙিন সুতো পরিয়ে “সদা সত্য কথা বলিবে”, “ভগবান ভরসা”, “যাকে রাখো সেই রাখে” ইত্যাদি লিখে লিখে বস্তির লোকেদের সেগুলো দান করেন। মাঝে মাঝে কাহার বস্তির অনিচ্ছুক শুয়োরগুলোকে ধরে এনে কুয়োতলায় তাদের জবরদস্তি সাবান মাখান। সন্ধেবেলায় ওঁর বাড়িতে ভজন গান হয়। সকালে দাঁতব্য হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করেন। খগাদার ডিসপেনসারিতে লোম-ওঠা পথের কুকুর, কুঁজে-ঘা-হওয়া বলদ এবং হাড্ডিসার মানুষ সকলেই চিকিৎসার জন্যে আসে এবং আশ্চর্য, কেউ কেউ ভালও হয়ে যায়।
খগাদা মৃতদার। ছেলেমেয়েও নেই। ভগাদা বিয়েই করেননি। দুই ভাইয়ের সুন-সান্নাটা সংসার। থাকবার মধ্যে একটা অ্যালসেশিয়ান কুকুর, তার নাম মোহিনী। চাকর-বাকর আছে, গাই-বয়েল, খেতি-খামার, খিদমদগার। আর আছে বারান্দায় দাঁড়ে বসা একটা কুৎসিত কাকাতুয়া। ভগাদার আদরের পাখি। কুকুরটাও আদরের। কাকাতুয়াটাকে ভগাদা আদর করে ডাকত ‘কাকু বলে। আমরা বলতাম “কাঁড়িয়া পিরেত”। ওদের বাড়ি ঢুকলেই কাকাতুয়াটা বলে উঠত, “ভাগো হিয়াসে, ভাগো হিয়াসে।”
খগাদা আধুনিক কবিতা, পশুপালন, বাজরা-মকাই, তাইচুং ও আই-আর-এইট ধান, ভগাদার ভবিষ্যৎ ইত্যাদি তাবৎ বিষয় নিয়েই আমাদের সঙ্গে জোর আলোচনা করতেন এবং গলার জোর বাড়ানোর জন্যে তেজপাতা-আদা-এলাচ : দেওয়া গোরখপুরী কায়দায় বানানো চা ও ভৈষালোটনের জঙ্গল থেকে আনানো খাঁটি ঘিয়ে ভাজা সেওই খাওয়াতেন।
সেদিন সকালে খগাদার বসবার ঘরে ঢুকতেই দেখি খগাদার মুখ গম্ভীর, থমথমে।
গুনছুঁচ ঢুকে গেছে কি বুড়ো আঙুলে?
বীরু নিজের বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বলল, খুব লেগেছে?
খগাদা বললেন, লেগেছে, তবে আঙুলে নয়, হৃদয়ে।
ঢোক গিলে বললাম, স্ট্রোক! মাইল্ড অ্যাটাক?
খগাদা বললেন, তার চেয়েও মারাত্মক।
আমরা বসে পড়ে সমস্বরে বললাম, কী, তবে কী?
খগাদা বললেন, চুরি।
কোথায়, কোথায়? চোর কোথায়? কী চুরি? বলে আমরা প্রায় চিৎকার করে উঠলাম।
এমন সময় ভগাদাকে দেখা গেল একটা লাল রঙের শর্টস্ পরে, কাবুলী জুতো পায়ে, খালি গায়ে কাকাতুয়াটাকে খাওয়াচ্ছেন নিজে হাতে, বারান্দায় এসে।
খগাদা আঙুল দেখিয়ে বললেন, ঐ যে কালপ্রিট, ঐ দাঁড়িয়ে আছে সশরীরে। সহোদর আমার। সাক্ষাৎ লক্ষ্মণ!
আমাদের খারাপ লাগল, বিশ্বাসও হল না। আপন ভাই কখনও চুরি করতে পারে?
খগাদা কী বলছে বুঝতে না পেরে ভগাদা সাঁ করে বারান্দা ছেড়ে সরে গেল ভিতরে। ধরে-থাকা খাঁচাটা হঠাৎ ছেড়ে দেওয়ায় কাকাতুয়ার খাঁচাটা জোরে নড়ে উঠল। কাকাতুয়াটা বলল, কাঁচকলা খা! কাঁচকলা খা! ভগাদাকেই বলল বোধহয়।
খগাদা আস্তে আস্তে বললেন, গত শনিবার রাতে এ-বাড়িতে যত কাঁসার ও রুপোর বাসন ছিল, সব চুরি করে নিয়ে গেছে চোরে, শুনেছ তোমরা?
বীরু বলল, সে কী? বাড়িতে বন্দুক ছিল না?
আমি বললাম, অত বড় অ্যালসেশিয়ান কুকুরও তো ছিল!
ছেল। খগাদা বললেন, ছেল সবই। কিন্তু বন্দুক রাখা ছেল গ্রীজ মাখানো অবস্থায় বেহালার বাক্সে। আর কুকুর মজাসে ঘুমোচ্ছিল।
আমরা বোকার মতো বললাম, কুকুর ঘুমোচ্ছিল মানে?
তাহলে আর বললুম কী? খগাদা সখেদে বললেন। তারপর আবার বললেন, যে বাড়িতে কুকুর ঘুমোয়, সে বাড়িতে চুরি হবে না?
এরপর গড়গড়ায় গয়ার তামাকে দুটো টান দিয়ে বললেন, বুঝলে ভায়ারা, রোজ রাতে পড়াশুনো করি, আর শুনতে পাই বারান্দায় মোহিনীর পায়ের পায়জোড়ের আওয়াজ। মোহিনীকে ভগা রুপোর পায়জোড় বানিয়ে দিয়েছিল। পা ফেললেই ঝুমুর ঝুমুর করে বাজে। আওয়াজ শুনতে পাই, কিন্তু এগারোটা বাজলেই দেখি আওয়াজ থেমে যায়। একদিন মনে সন্দ হওয়াতে পা টিপে টিপে ভগার ঘরের সামনে গিয়ে দেখি ভগা মশারির মধ্যে অঘোরে ঘুমোচ্ছে, আর মেঝেতে শুয়ে মোহিনীও দিব্যি নাক ডাকাচ্ছে। আমি ডাকলুম, ভগা! তাতে ‘কে রে’ বলেই ভগা উঠে বসে জানলার ধারে আমায় দেখতে পেয়েই ঘুমন্ত মোহিনীর পেটে মারলে ক্যাঁক করে এক লাথি। ঘুমঘোরে লাথি খেয়ে মোহিনী তো মারলে বডি থ্রো–
বীরু বলল, আর ভগাদা?
ভগাদা? বলে, খগাদা বিদ্রুপের হাসি হাসলেন। বললেন, ভগা আবার তক্ষুনি শুয়ে পড়ল।
তারপর বললেন, তোমরাই বলো, এ বাড়িতে চুরি হবে না তো কোন্ বাড়িতে হবে?
আমরা সত্যিই বড় চিন্তায় পড়লাম খগাদার জন্যে। সরি, ভগাদার জন্যে। আসলে ভগাদা মাঝে মাঝেই আমাদের এবং খগাদাকে ঝামেলায় ফেলতেন।
একদিন কলেজ থেকে বাড়ি ফিরেই শুনলাম, খগাদা আমাদের জরুরি তলব দিয়েছেন।
আমরা দৌড়ে গেলাম। দেখি, খগাদার অবস্থা খুব খারাপ। কোলে বাট্রান্ড রাসেলের কন্কোয়েস্ট অব্ হ্যাপিনেস’ বইটানা আধ-খোলা পড়ে আছে, আর খগাদার চোখের কোণে জল চিকচিক করছে।
বীরু বলল, খগাদা, কী? দুঃখ কিসের?
খগাদা বললেন, আর কী, একমাত্র ভাইটাকে বুঝি হারালাম এবার!
কী, হয়েছে কী? আমি উত্তেজিত হয়ে শুধোলাম।
খগাদা বললেন, ভগা আর ওর বন্ধু গিদাইয়া পদ্মার রাজার বিলে হাঁস মারতে গেছে সেই ভোর চারটেয় বাড়িতে মশলা বাটতে বলে গেছে। হাঁসের শিকাবাব বানাবে বলে শিক ঘষামাজা করে রাখতে বলেছে, টক দই, পেঁপে, গরমমশলা, ভাঙা পিরিচ, সবকিছুর জোগাড় রেখে গেছে। আর দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতে চলল, এখনও তাদের দেখা নেই। নির্ঘাত কোনও অঘটন ঘটেছে। আমার পায়ের গেঁটে বাতটা বেড়েছে কয়েকদিন হল। আজ আবার অমাবস্যা। রোজ রসুন খাই, তবু ব্যথা যায় না। আমি তো চলচ্ছক্তিরহিত। তোমরা বাবা যাও, একটু। আমার জীপগাড়িটা নিয়ে যাও। ভগা গিদাইয়াকে নিয়ে মোটর সাইকেলে করে গেছে।
বীরু বলল, নো-প্রবলেম। আপনি চিন্তা করবেন না খগাদা, আমরা বন্দোবস্ত করছি। তার আগে আমি চট করে পোস্ট অফিস থেকে পদ্মার রাজবাড়ির ম্যানেজারকে একটাফোন করে খবর নিয়ে নিই। তাঁকে আমি চিনি, আমার কাকার বন্ধু।
খগাদা বললেন, বাস বাস, তাহলে তো কথাই নেই। এই নাও, টাকা নিয়ে যাও। বলেই, কোমরের গেঁজ থেকে একটা লাল রঙের নাইলনের মোজা বের করে তার থেকে একটা দশটাকার নোট দিলেন বীরুকে।
বীরু আমাকে বলল, তুই থাক। খগাদা নিডস্ কম্পানি।
খগাদা বললেন, বুঝলে ভায়া, আজ কত কথাই মনে পড়ছে। ভগা যখন হাসপাতাল থেকে মায়ের সঙ্গে বাড়ি এল, তখন ওকে দেখতে একেবারে বাচ্চা একটা খরগোশের মতো ছিল। কী গাবলুগুবলু! তার উপর আবার খিল খিল করে হাসত। আমার চেয়ে কত ছোট। কিন্তু পড়াশোনা করল না, কিছুই করল না, জীবনটাকে নষ্ট করল পাখি আর কুকুর নিয়ে। আমিই এখন ওর মা, ওর বাবা, ওর দাদা, সব। কী বিপদ হল কে জানে। বিলে কি ডুবে মরল, না কি সাপে কামড়াল?
একটু পর ক্রিং ক্রিং করে সাইকেলের ঘন্টি বাজিয়ে চাকায় কির শব্দ তুলে বীরু ফিরল।
খগাদা একবার দাঁড়াবার চেষ্টা করেই মুখ বিকৃত করে ‘উঃ মাগো’ বলে পায়ের ব্যথায় বসে পড়লেন।
বসেই বীরুর মুখের দিকে চেয়ে বললেন, খবর পেলে?
বীরু অধোবদনে দাঁড়িয়ে গম্ভীর মুখে বলল, হুঁ।
কী? খগাদা চিৎকার করে উঠলেন। তারপর বললেন, বলে ফেল সোজাসুজি। আছে, না নেই? তারপরই দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, ভগা রে! আমার ভগাবাবু!!
বীরু বলল, ভগাদা আছে। কিন্তু রাজার কয়েদখানায়।
হোয়াট? বলে খগাদা আবার উঠে দাঁড়াতে গিয়েই ‘গেছি গেছি গেছি বলে বসে পড়লেন।
তারপর হাতের ‘কনকোয়েস্ট অব হ্যাপিনেস’টাকে মাটিতে ছুঁড়ে বললেন, হোয়াই? হাউ কাম?
বীরু বলল, বিলের ধারে রাজার পোষা হাতি চরছিল, ভগাদা তাকে গুলি করেছে।
হাতিকে? গুলি? পাখি-মারা ছররা দিয়ে? ইমপসিবল্! নিশ্চয়ই অ্যাকসিডেন্ট। তা বলে কয়েদখানায়? খগা সরকারের ভাই কয়েদখানায়?
বীরু, বীরুর কাকা ও আমি যখন খগাদার জীপ নিয়ে গিয়ে পদ্মার রাজার কয়েদখানা থেকে পঁচিশ টাকা জরিমানা দিয়ে ভগাদা, গিদাইয়া আর মোটর সাইকেলটাকে ছাড়িয়ে আনলাম, তখন রাত হয়ে গেছে।
আসবার পথে বীরু বলল, ভগাদা, কী করে এমন হল? হাতি কি তোমাকে তেড়ে এসেছিল?
ভগাদা বললেন, আরে না-না। এই গিদাইয়া ইডিয়টার জন্যেই তো।
গিদাইয়া মাথা ঘুরিয়ে টিকি নেড়ে মহা প্রতিবাদ জানাল।
ভগাদা বললেন, বুঝলি টিকি নেড়ে মহা প্রতিবাদ জানাল।
ভগাদা বললেন, বুঝলি, বিলে এক ঝাঁক পিটেইল হাঁস ছিল। একটা পুটুম্ ঝোঁপের পাশে শুয়ে এই করছিলাম। ভাবছিলাম, লাইনে পেলেই একেবারে গদাম করে ঝেড়ে দেব, গোটা ছয়েক উল্টে যাবে। এমন সময়…
আমি বললাম, এমন সময় কী?
ভগাদা বললেন, এমন সময় গিদাইয়া কানের কাছে ফিসফিস করে বলল, ভগা! ওয়াইল্ড এলিফ্যান্ট। তাকিয়ে দেখি, আমাদের পাশেই একটা হাতি দাঁড়িয়ে ভোঁস-ভোঁস করে শুড় ঘুরিয়ে নিশ্বাস নিচ্ছে আর কান নাড়াচ্ছে। আমার মন বলল, নিশ্চয়ই পোষা হাতি; রাজার। কিন্তু গিদাইয়া বলল, এক-একটা দাঁত– পাঁচ-পাঁচ হাজার টাকা। অত হাজার টাকার কথা শুনেই আমার মাথা ঘুরে গেল। দিলাম দেগে এক নম্বর ছররা।
আমি রুদ্ধশ্বাসে শুধোলাম, তারপরে কী হল?
তারপর আর কী! হাতি বলল, প্যাঁ-অ্যা-অ্যা-অ্যা-অ্যা। আর আমি ও গিদাইয়াও একসঙ্গে ভ্যাঁ–অ্যা-অ্যা-অ্যা।
বীরু অবাক হয়ে বলল, কেঁদে ফেললে? এ মা, এত বড় লোক হয়ে কেঁদে ফেললে?
ভগাদা বললেন, হুঁ-হুঁ বাবা, কান্না পেলেও না যদি কাঁদো তবে সঙ্গে সঙ্গে ইসকিমিয়া, মায়াকার্ডিয়াক অ্যাটাক। হার্ট এক্কেরে কিমা। জানিস না তোরা কিছুই।
বীরু বলল, তারপর?
তারপর আর কী? হাতি এসে ঘাড়ে পড়ার আগেই মাহুত আর রাজার পেয়াদা এসে ঘাড়ে পড়ল। বন্দুক কেড়ে নিল। আর কী রদ্দা, কী রদ্দা!
হাতিটাকে কোথায় মেরেছিলেন? আমি শুধোলাম।
ভগাদা বললেন, এই করেছিলাম কানের পাশেই নিয়ম-মাফিক।
গিদাইয়া এতক্ষণ পর কথা বলল। বলল, কিন্তু কুল্লে চার দানা ছররা গিয়ে লেগেছিল হাতির সামনের পায়ের গোড়ালিতে।
ভগাদা চটে উঠে বলল, শাট আ। দোস্ত তো নয়, সাক্ষাৎ দুশমন।
এই ঘটনার কিছুদিন পরই খগাদা আমাদের নেমন্তন্ন করে খুব একচোট খাওয়ালেন। ভগাদা চাকরিতে জয়েন করেছেন। অডার সাপ্লাইয়ের ব্যবসা। নিজেই চেষ্টা-চরিত্র করে যোগাড় করেছেন। এতদিনে ভাইয়ের একটা গতি হল। সকলেই খুশি, আমরাও। ভগাদা রোজ সময়মত প্যান্ট আর হাওয়াইন শার্ট পরে অফিস যান।
দিন পনরো বাদে খগাদা আবার আমাদের জরুরি তলব দিলেন। গেলাম। বুঝলাম, আবার কেস গড়বড়।
খগাদা বললেন, আবার একটা উপকার করতে হবে।
আমরা বললাম, বলুন কী করতে পারি! ভগাদা কি আবার কোনও ঝামেলা…
খগাদা বললেন, শোনো আগে। চাকরি করছিল ভগা, খুশি ছিলাম কত। কিন্তু গত কয়েকদিন অফিস যাচ্ছিল না। প্রথমে বলছিল পেটে ব্যথা। নাক্স-ভমিকা থারটি দিলাম। তারপর বলতে লাগল গায়ে ব্যথা। আর্নিকা দিলাম। তারপর বলল, রাতে ঘুম হয় না। কালিফস্ দিলাম। তাতে ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোবার কথা, কিন্তু সমানে কড়িকাঠের দিকে চেয়ে ভায়া আমার শুয়ে থাকে। কথাও বলে না, খায়ও না। তারপর ওআরস্ট অব অল, কাল থেকে পলাতক। কোথায় যে চলে গেল না বলে-কয়ে!
বীরু হঠাৎ বলল, চাকরির ব্যাপারটা একটু খোঁজ করলে হত না? সেখানে কোনও গোলমাল?
খগাদার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললেন, ব্রিলিয়ান্ট! সাধে কি বলি, তোমাদের মতো ছেলে হয় না।
বীরু আমাকে বলল, চল, এক্ষুনি ব্যাপারটা জেনে আসা যাক।
খগাদার কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে বীরু বেরিয়ে পড়ল সাইকেলে আমাকে ডাবল ক্যারি করে।
সবজিমন্ডির পাশে মসজিদ, মসজিদের থেকে খানিকটা দূরে ক্কালু মিঞার কাবাবের দোকান, তার পাশে একটা ছোট দোকানঘর– সবুজের উপর সাদায় লেখা সাইনবোর্ড ঝুলছে, ইন্টারন্যাশনাল সাপ্লায়ার্স। কিন্তু সেই আন্তজাতিক প্রতিষ্ঠানের কেরোসিন তেলের টিন দিয়ে তৈরি দরজাটাতে একটা মস্ত বড় তালা ঝুলছে।
আমরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম সাইকেল থেকে নেমে। ইন্টারন্যাশনাল সাপ্লায়ার্সের উল্টোদিকে একটা দর্জির দোকান। খয়েরি আর সাদা খোপ-খোপ লুঙ্গি আর বেগনে কামিজ পরে মাথায় সাদা টুপি চড়ানো কালো চাপ-দাড়িওয়ালা দর্জি আপনমনে ঝটপট করে পা-মেশিনে রজাইয়ের ওয়াড় সেলাই করে যাচ্ছিল।
আমরা গিয়ে একটু কেশে দাঁড়ালাম।
দর্জি মুখ তুলে নিকেলের ফ্রেমের চশমার কাঁচের ফাঁক দিয়ে চোখ নাচিয়ে বলল, ফরমাইয়ে।
বীরু বলল, খাস কাম কুছ নেহী। এই যে উল্টোদিকের অফিসটা, সেটা বন্ধ কেন? তালা ঝুলছে কেন?
দর্জি বলল, দফতর বন্ধু হ্যায়। উঠ গ্যায়া।
উঠে গেছে মানে? আমরা শুধোলাম।
দর্জি বলল, জী হাঁ। তারপর ডান হাতের তিনখানা আঙুল বীরুর নাকের সামনে নেড়ে নেড়ে বলল, আপিস তো ছিল দুজনের হেডবাবু গিরধারী পাণ্ডে আর অ্যাসিস্ট্যান্ট ভগা সরকার। সেদিন কী নিয়ে কথা কাটাকাটি হতে অ্যাসিস্ট্যান্ট গিয়ে হেডবাবুর মাথায় হঠাৎ কাঠের রুলার দিয়ে মারল এক বাড়ি। সাথে সাথ মাথা ফট। হেডবাবু হাসপাতালে আর অ্যাসিস্ট্যান্ট ফেরার। আপিস আর চালাবে কে? কিওয়ারি বন্ধু।
আমরা ফিরলাম। খগাদা উদগ্রীব হয়ে বসেছিলেন। বললেন, কী খবর?
বীরু গম্ভীরমুখে বলল, আপিস উঠে গেছে। হেডবাবু হসপিটালে, অ্যাসিস্ট্যান্ট এবস্কন্ডিং।
খগাদা প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে “মার্ডারার, মার্ডারার, কোথায় গেলি, কোথায় গেলি” বলেই দৌড়ে বারান্দার দিকে গেলেন, যেন ভগাদা বারান্দাতেই বসে আছেন।
খগাদা বারান্দাতে গিয়ে পৌঁছতেই ভগাদার ঠোঁটকাটা কাকাতুয়াটা খ্যামূখেনে গলায় বলে উঠল, হাইপারটেশান্। হাইপারটেশান্!
.
লাওয়ালঙের বাঘ
ঋজুদার সঙ্গে সীমারীয়ার ডাকবাংলোয় আজ রাতের মতো এসে উঠেছি। আমরা যাচ্ছিলাম কাড়গুতে, চার রাস্তায়; কিন্তু কলকাতা থেকে একটানা জীপ চালিয়ে এসে গরমে সবাই কাবু হয়ে পড়েছিল বলে রাতের মতো এখানেই থাকা হবে বলে ঠিক করল ঋজুদা।
সবাই বলতে, ঋজুদা, অমৃতলাল আর আমি।
এখন রাত আটটা হবে। শুক্লপক্ষ। বাইরে ফুটফুট করছে জ্যোৎস্না। চৌকিদার হ্যারিকেন জ্বালাবার তোড়জোড় করছিল, ঋজুদা বলল, তুমি বাবা আমাদের একটু খিচুড়ি আর ডিমভাজা বানিয়ে দাও। অমৃতলালও গিয়ে বাবুর্চিখানায় জুটেছে। আলুকা ভাত্তা বড় ভাল বানায় অমৃতলাল, ওর নানীর কাছ থেকে শিখেছিল। আলুসিদ্ধ, তার মধ্যে ঘি, কুচিকুচি কাঁচা পেঁয়াজ আর কাঁচালঙ্কা দিয়ে এমন করে রগড়ে রগড়ে মাখত যে, তার নাম শুনলেই আমার জিভে জল আসত।
ঋজুদা ঝাঁকড়া সেগুনগাছের নীচের কুয়োতলায় দাঁড়িয়ে নিজেই লাটাখাম্বাতে জল তুলে ঝপাং ঝপাং করে বালতি বালতি জল ঢেলে চান করছিল। চাঁদেরআলোর বন্যা বয়ে-যাওয়া বারান্দার ইজিচেয়ারে বসে ছিলাম আমি। একা। ঋজুদা বলেছিল, তোর আর রাতে চান করে দরকার নেই। কোলকাত্তীয়া বাবু, শেষে সর্দি-ফুর্দি লাগিয়ে ঝামেলা বাধাবি।
সামনে লালমাটির পথটা চলে গেছে ডাইনে টুটিলাওয়া-বানদাগ হয়ে হাজারীবাগ শহরে। বাঁয়ে কয়েক মাইল এগিয়ে গেলেই বাঘড়া মোড়। সেখান থেকে বাঁদিকে গেলে পালামো’র চাঁদোয়া–টোড়ি। ডানদিকে গেলে চারা। এই সীমারীয়া থেকেই একটা কাঁচা রাস্তা চলে গেছে চারাতে। আরও একটা পথ টুটিলাওয়া আর সীমারীয়ার মাঝামাঝি মূল পথ থেকে বেরিয়ে গেছে লাওয়াল।
বাইরে নানারকম রাতচরা পাখি ডাকছে। সকলের নাম জানি না আমি। ঋজুদা জানে। আমি শুধু টী-টী পাখির ডাক চিনি। আসবার সময় সন্ধে হওয়ার আগে জঙ্গলের মধ্যে যে জায়গাটায় জীপ খারাপ হয়ে গিয়েছিল, ঠিক সেখানে একদল চাতক পাখি ফটিক-জল-ফটিক-জল করে ঘুরে ঘুরে একটা পাতা ঝরা ফুলে-ভরা শিমুল গাছের উপরে উড়ছিল। ঐ শিমুল গাছের সঙ্গে ওদের আত্মীয়তাটা কিসের তা বুঝতে পারিনি। আত্মীয়তা নিশ্চয়ই কিছু ছিল।
এরকম হঠাৎ-থামা, হঠাৎ-থাকা জায়গাগুলোর ভারী একটা আকর্ষণ আছে। আমার কাছে। এরা যেন পাওয়ার হিসেবের মধ্যে ছিল না, এরা যেন ঝড়ের-আমের মতো; পড়ে-পাওয়া। অথচ কত টুকরো টুকরো ভাললাগা এই সমস্ত হঠাৎ পাওয়ায় ঝিনুকের মধ্যে নিটোল সুন্দর মুক্তোর মতো।
একটা হাওয়া ছেড়েছে বনের মধ্যে। শুকনো শালপাতা উড়িয়ে নিয়ে, গড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে নালায়-টিলায়; ঝোপে-ঝাড়ে। দূরের পাহাড়ে দাবানল লেগেছে। আলোর মালা জ্বলছে। অনেকক্ষণ চেয়ে থাকলে দেখা যায় পাহাড়ে পাহাড়ে মালাবদল হচ্ছে। এমনি করে কী পাহাড়দের বিয়ে হয়? কে জানে?
হাওয়ায় হাওয়ায়, ঝরে-যাওয়া পাতায়, না-ঝরা পাতায় কত কী ফিসফিসানি উঠছে। চাঁদের আলোয় আর হাওয়ায়-কাঁপা ছায়ায় কত কী নাচ নাচছে এই রাত–সাদা-কালোয়, ছায়া-আলোয়। কত কী গাছ উঠছে। গাছেদের তো প্রাণ আছে, ওদের গানও আছে, কিন্তু ওদের ভাষা তো আমরা জানি না–কোনও স্কুলে তো ওদের ভাষা শেখায় না। কেন যে শেখায় না! ভারী খারাপ লাগে ভাবলে।
ঋজুদা স্নান করছে তো করছেই। কতক্ষণ ধরে যে স্নান করে ঋজুদাটা! যখন ঋজুদার স্নান প্রায় শেষ হয়ে এসেছে বাবুর্চিখানা থেকে অমৃতলালের গুরুমুখী গানের নিচু গুনগুনানি ভেসে আসছে খিচুড়ি রান্নার শব্দ ও গন্ধের সঙ্গে, এমন সময় মশাল হাতে একদল লোককে আসতে দেখা গেল টুটিলাওয়ার দিক থেকে। লোকগুলো হাজারীবাগী–টাঁড়োয়া-গাড়োয়া ভাষায় উঁচু গলায় কী সব বলতে বলতে আসছিল।
চেয়ার ছেড়ে উঠে বারান্দার থামে হেলান দিয়ে, উৎকর্ণ হয়ে ঐ দিকে চেয়ে রইলাম।
লোকগুলো যখন বাংলোর সামনাসামনি এল, তখন ঋজুদা বারান্দায় এসে ওদের হিন্দীতে শুধোল, কী হয়েছে ভাই?
ওরা সমস্বরে বলল, বড়কা বাঘোয়া।
ব্যাপারটা শোনা গেল।
বড় একটা বাঘ, গরু চরাতে-যাওয়া একটা পনেরো-ষোলো বছরের ছেলেকে ঠিক সন্ধের আগে আগে একটা নালার মধ্যে ধরে নিয়ে গেছে।
গরুগুলো ভয়ে দৌড়ে গ্রামে ফিরতেই ওরা ব্যাপার বুঝতে পেরে ছেলেটার খখাঁজে যায়। গাঁয়ের শিকারী তার গাদা বন্দুক নিয়ে জনাকুড়ি লোক সঙ্গে নিয়ে মশাল জ্বালিয়ে রক্তের দাগ দেখে দেখে নালার কাছে যেতেই বাঘটা বিরাট গর্জন করে তেড়ে আসে নালার ভিতর থেকে। তাতে ঐ শিকারী গুলি করে। গুলি নাকি লাগেও বাঘের গায়ে–কিন্তু বাঘটা ঐ শিকারীর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার মাথাটা একেবারে তিলের নাড়র মতো চিবিয়ে, সকলের সামনে তাকে মেরে ফেলেই সঙ্গে সঙ্গে আবার নালার অন্ধকারে ফিরে যায়।
ওরা বলল, ছেলেটাকে তো এতক্ষণে মেরে ফেলেছেই, খেয়েও ফেলেছে হয়তো। ওরা কী করবে ভেবে না পেয়ে এখানে ফরেস্টারবাবুকে খবর দিতে এসেছে।
ঋজুদা চুপ করে ওদের কথা শুনছিল। জনাকয় লোক বাংলোর সামনে দাঁড়িয়েছিল, অন্যরা ফরেস্টারবাবুর বাংলোর দিকে চলে গেল।
আমার আর তর সইল না। আমি ঋজুদাকে দেখিয়ে ওদের বলে ফেললাম, কোই ডর নেহী–ঈ বাবু বহত্ জবরদস্ত শিকারী হ্যায়।
এ কথা বলতে-না-বলতেই ওদের মধ্যে কিছু লোক ফরেস্ট অফিসে দৌড়ে গেল এবং কিছুক্ষণের মধ্যে ফরেস্টারবাবুকে সঙ্গে করে ফিরে এল সকলে। ওঁরা সকলে মিলে ঋজুদাকে বার বার অনুরোধ করলেন। ছেলেটা গ্রামের মাহাতোর ভাতিজা। মৃতদেহের কিছু অংশ না পেলে দাহ করা যাবে না এবং তাহলে ছেলেটার আত্মা চিরদিন নাকি জঙ্গলে-পাহাড়ে, টাঁড়ে-টাঁড়ে ঘুরে বেড়াবে, ভূত হয়ে যাবে।
আমি রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে পড়লাম। ঋজুদার সঙ্গে এ পর্যন্ত ওড়িশার জঙ্গলে অনেক ঘুরলেও কখনও এমন সদ্য মানুষমারা বাঘের সঙ্গে মোলাকাতের অভিজ্ঞতা হয়নি। ১০২
গোলমালটা হল ঋজুদাকে নিয়েই। ঋজুদা বলল, রুদ্র, তুমি যাবে না। তুমি আর অমৃতলাল দুজনেই থাকবে এখানে।
অমৃতলাল বলল, নেহী বাবু, ঈ ঠিক নেই হ্যায়। একেলা যানা নেই। চাহিয়ে। দু বন্দুক রহনা জরুরী হ্যায়।
তখন ঋজুদা অধৈর্য গলায় অমৃতলালকে বলল, কিন্তু রুদ্র যে বড় ছেলেমানুষ– ওর কিছু হলে ওর বাবা-মাকে কী বলব আমি?
আমি সকলের সামনেই ঋজুদার পা জড়িয়ে ধরে বললাম, ঋজুদা, আমাকে নিয়ে চলো, প্লিজ। তুমি তো সঙ্গেই থাকবে। তোমার যা হবে আমারও তাই হবে।
ঋজুদা কিছুক্ষণ চুপ করে আমার দিকে চেয়ে রইল। বলল, তুই ভারী অবাধ্য হয়েছিস। তারপরই বলল, আচ্ছা চল।
জীপে যে-কজন লোক ধরে, তাদের নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম, লাওয়ালঙের রাস্তায়। অমৃতলাল জীপ চালাচ্ছিল তখন। ঋজুদা ফোরফিটি-ফোর হানড্রেড দোনলা রাইফেলটা নিয়েছিল। আমার হাতে দোনলা বারো বোরের বন্দুক। দুটো অ্যালফাম্যাকস্ এল-জি আর দুটো লেথা বল নিয়েছি সঙ্গে।
গরমের দিন। জঙ্গল একেবারে পাতলা হয়ে গেছে পাতা ঝরে। বর্ষার শেয়ে বড় বড় গাছের নীচে নীচে যে-সব আগাছা, ঝোঁপঝাড়, লতা-পাতা গজিয়ে ওঠে এবং শীতে যেগুলো ঘন হয়ে থাকে যাদের ঋজুদা বলে ‘আন্ডার গ্রোথ’– সে সব এখন একেবারেই নেই। জীপের আলোর দুপাশে প্রায় একশো-আশি ডিগ্রী চোখ চলে এখন।
একটা খরগোশ রাস্তা পেরুল ডানদিক থেকে বাঁদিকে। পর পর দুটো লুরির জ্বলজ্বলে সবুজ চোখ দেখা গেল। একটু পরেই আমরা পথ ছেড়ে একটা ছোট পায়ে-চলা পথে ঢুকে গ্রামটাতে এসে পৌঁছলাম। জীপের আওয়াজ শুনেই লোকজন ঘরের বাইরে এল। জীপটা ওখানেই রেখে দেওয়া হল। তারপর গ্রামের যে মাহাতো, তাকে ঋজুদা বলল পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে আমাদের।
যে শিকারীকে বাঘ মেরে ফেলেছে, তাকে খাঁটিয়ার উপর একটা সাদা চাদর দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছিল। মাটির দেওয়াল আর খাপরার চালের বাড়িগুলো থেকে মেয়ে ও বাচ্চাদের কান্না শোনা যাচ্ছিল। ঋজুদা সেই মৃতদেহের কাছে গিয়ে চাদর সরিয়ে লণ্ঠন দিয়ে কী যেন দেখল ভাল করে। তারপর ফিরে এসে বলল, চল্ রুদ্র।
গ্রামের লোকেদের যথাসম্ভব কম কথা বলতে ও আওয়াজ করতে অনুরোধ করে ঋজুদা আর আমি মাহাতোর সঙ্গে এগোলাম। উত্তেজনায় আমার গা দিয়ে তখনই দরদর করে ঘাম বেরুচ্ছিল, হাতের তেলো ঘেমে যাচ্ছিল। বারবার খাকি বুশ শার্টের গায়ে ঘাম মুছে নিচ্ছিলাম।
জঙ্গলের বেশির ভাগই শাল। মাঝে মাঝে আসন, কেঁদ, গনহার এসবও আছে। আমলকী গাছ আছে অনেক। জঙ্গলের মধ্যে মধ্যে এক-এক ফালি চাষের জমি। হয়তো শীতে কিতারী, অড়হর, কুন্থী বা গেঁহু লাগিয়েছিল। এখন কোনও চিহ্ন নেই তার। মাটি ফেটে চৌচির হয়ে আছে।
আলো না-জ্বালিয়ে, আমরা নিঃশব্দে শুকনো পাতা না-মাড়িয়ে, পাথর এড়িয়ে হাঁটছি। বন্দুকে গুলি ভরে নিয়েছি। ঋজুদার কথামতো দু নলেই এল-জি পুরে নিয়েছি। খুব কাছাকাছি থেকে গুলি করতে হলে নাকি এলজিই ভাল। ঋজুদাও রাইফেলের দু ব্যারেলে সক্ট-নোজড় বুলেট পুরে নিয়েছে। ঋজুদার রাইফেলের সঙ্গে একটা ক্ল্যাম্পে ছোট একটা টর্চ লাগানো আছে ক্ল্যাম্পের সঙ্গে আটকানো একটা লোহার পাতে নিশানা নেবার সময় বাঁ-হাতের আঙুল ছোঁয়ালেই টর্চটা জ্বলে ওঠে। আমার বন্দুকে আলো নেই। এমন জ্যোৎস্নারাতে বন্দুক ছুঁড়তে আলো লাগে না। বন্দুক ছোঁড়া রাইফেল ছোঁড়ার চেয়ে অনেক সহজ।
কিছুদূর গিয়ে আমরা একটা উপত্যকায় এসে পৌঁছলাম। জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে শান্ত উদোম উপত্যকা। দূরে পিউ-কাঁহা পিউ-কাঁহা করে রাতের বনে শিহর তুলে পাখি ডাকছে। কী চমৎকার সুন্দর পরিবেশ। ভাবাই যায় না যে, এই আলোর মধ্যের ছায়ার আড়ালে মৃত্যু লুকিয়ে আছে অমন মর্মান্তিক মৃত্যু। দু-দু’জন লোক আজ সন্ধে থেকে এখানে মারা গেছে, বলতে গেলে খুন হয়েছে, অথচ কী সুন্দর পাখি ডাকছে; হাওয়ায় মহুয়া আর করৌনজ ফুলের গন্ধ ভাসছে কী দারুণ।
মাহাতো আঙুল দিয়ে দূরে যে জায়গাটা থেকে বাঘ নালা ছেড়ে উঠে এসে শিকারীকে আক্রমণ করেছিল, সেই জায়গাটা দেখিয়ে দিল। ঋজুদা ফিসফিস করে বলল, সামনে যে পিপুল গাছটা আছে, তাতে তুমি চড়ে বসে থাকো। আমরা ডানদিকে গিয়ে বাঘের যে-জায়গায় থাকার সম্ভাবনা, সে-জায়গা থেকে কম করে তিনশ গজ দূরে নালায় নামব।
তারপর আর কিছু না বলে ঋজুদা এগিয়ে চলল। পরক্ষণেই, দাঁড়িয়ে পড়ে, মাহাতোকে বলল, দিনের আলো ফোঁটার আগেও যদি আমরা না ফিরি, তাহলে অমৃতলালকে ও গাঁয়ের লোকদের নিয়ে আমাদের খুঁজতে এসো।
কথাটা শুনে মাহাতো খুব খুশি হল না, চাঁদের আলোয় তার মুখ দেখেই তা বোঝা গেল।
এরপর ঋজুদা আর আমি সেই চন্দ্রালোকিত উপত্যকায় দুটি ছায়ার মতো, নিঃশব্দে দূরের শুয়ে-থাকা ঘন কালো ছায়ার মতে, নালাটির দিকে এগিয়ে যেতে লাগলাম।
ঋজুদা শুধু একবার ফিসফিস করে বলল, ভয় পেয়ে পিছন থেকে আমাকে গুলি করিস না যেন। নালায় নেমে আমার পাশে পাশে হাঁটবি পিছনে নয়। একটুও শব্দ না করে। প্রত্যেকটি পা ফেলার আগে কোথায় পা ফেলছিস, তা দেখে ফেলবি এক পা এগোবার আগে সামনে ও চারপাশে ভাল করে দেখবি। কান খাড়া রাখবি, নালার মধ্যে চোখের চেয়ে কানের উপরই বেশি নির্ভর করতে হবে। নালার মধ্যে হয়তো অন্ধকার থাকবে। তোর বন্দুকে আলো থাকলে ভাল হত।
যাই হোক, তখন আর কিছু করার নেই। আশা করতে লাগলাম, পাতা-ঝরা গাছগুলোর ফাঁকফোঁক দিয়ে নালার মধ্যে কিছুটা আলো হয়তো চুঁইয়ে আসবে। গুলি খাক আর না-ই খাক, বাঘ যে নালার মধ্যেই থাকবে, এমন কোনও কথা নেই। যদি নালার মধ্যে থাকে, তাহলে নালার কোন্ জায়গায় থাকবে তারও স্থিরতা নেই। তা ঋজুদা ভাল করে জানে বলেই এত সাবধান হয়ে নালার প্রায় শেষ প্রান্তের দিকে আমরা এগোচ্ছি।
দেখতে দেখতে নালার মুখে চলে এলাম। শুকনো বালি, চাঁদের আলোয় ধবধব করছে। আমাকে হুঁশিয়ার থাকতে বলে ঋজুদা হাঁটু গেড়ে বসে নালার বালি পরীক্ষা করে দেখল। নালা থেকে যে বাঘ বেরিয়ে গেছে তেমন কোনও পায়ের চিহ্ন দেখা গেল না। খুব বড় একটা বাঘের পায়ের দাগ ছাড়াও শুয়োর, শজারু, কোট্রা হরিণ ইত্যাদির অনেক পায়ের দাগ দেখা গেল। বাঘ ভিতরে। ঢুকেছে, কিন্তু এদিক দিয়ে বাইরে বেরোয়নি।
নালায় পৌঁছনোর আগে অবধি একটা টী-টী পাখি আমাদের মাথার উপরে ঘুরে ঘুরে উড়ে উড়ে টিটির-টি–টি-টি-টি-টি করে ডাকতে ডাকতে সারা বনে আমাদের আগমন বার্তা জানিয়ে দিল। আমার মন বলছিল, বাঘ একেবারে খবর পেয়ে তৈরি হয়েই থাকবে।
এবারে আমরা নালার মধ্যে ঢুকে পড়েছি।
দুপাশে খাড়া পাড়। কোথাও বা খোয়াই, পিটিসের ঝোঁপ, আমলকীর পত্রশূন্য ডালে থোকা-থোকা আমলকী ধরে আছে। নালার মধ্যে মধ্যে একটা জলের ধারা বয়ে এসেছে ও-পাশ থেকে। কোথাও সে-জলে পায়ের পাতা ভেজে– কোথাও বা তাও নয়–শুধু বালি ভিজে রয়েছে।
কোনও সাড়াশব্দ নেই– শুধু একরকম কটকটে ঝিঁঝির একটানা ঝাঁঝ আওয়াজ ছাড়া।
একটা বাঁক নিলাম। ঋজুদা এক-এক গজ পথ যেতে পাঁচ মিনিট করে সময় নিচ্ছে।
যতই এগোতে লাগলাম, ততই জলের ধারাটা গম্ভীর হতে লাগল। কোথাও কোথাও হাঁটুসমান জল পাথরের গভীরে জমে আছে। তার মধ্যে ব্যাঙাচি, কালো কালো লম্বা গোঁফওয়ালা জলজ পোকা। আমাদের পায়ের শব্দের অনুরণনে একটা ছোট ব্যাঙ জলছড়া দিয়ে দৌড়ে গেল জলের মধ্যে।
যতই এগোচ্ছি, ততই নিস্তব্ধতা বাড়ছে। এত জানোয়ারের পায়ের দাগ দেখলাম নালায় ঢোকার সময় বালিতে, কিন্তু কারও সঙ্গেই দেখা হল না এ পর্যন্ত। কোন্ মন্ত্রবলে তারা যেন সব উধাও হয়ে গেছে।
ঋজুদার কান চোখ তীক্ষ্ণ হয়ে আছে। ঋজুদার হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে বাঘ নালার মধ্যেই আছে। বন্দুকটা শুটিং-পজিশনে ধরে সেটি ক্যাচে বুড়ো আঙুল ছুঁইয়েই আছি আমি– যাতে প্রয়োজনে এক মুহূর্তের মধ্যে গুলি করতে পারি।
বোধহয় এক ঘণ্টা হয়ে গেছে আমরা নালাটার মধ্যে ঢুকেছি। এতক্ষণে বেশ অনেকখানি ভিতরে ঢুকে থাকব। নালার মধ্যেটাকে আলো-ছায়ার কাটাকুটি করা একটা ডোরাকাটা সতরঞ্জি বলে মনে হচ্ছে।
হঠাৎ বুকের মধ্যে চমকে দিয়ে কাছ থেকে হুপ-হুপ-হুপ-হুপ করে একসঙ্গে অনেকগুলো হনুমান ডেকে উঠল। আমরা যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম, সেখান থেকে পঁচিশ গজ দূরের একটা বড় গাছের উপরের ডালে ডালে হনুমানদের নড়ে-চড়ে বসার আওয়াজ, ডালপালার আওয়াজ শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে ঋজুদা আমার গায়ে হাত ছুঁইয়ে আমাকে নালার বাঁদিকের পাড়ের দিকে সরে আসতে ইশারা করল। আমি সরে আসতেই, আমার সামনে ছায়ার মধ্যে একটা বড় পাথরের উপর বসে, দু হাঁটুর উপরে রাইফেলটা রেখে সামনের দিকে চেয়ে রইল ঋজুদা তীক্ষ্ণ চোখে।
নালাটা সামনে একটা বাঁক নিয়েছে।
হনুমানদের হুপহাপ আওয়াজ থেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সামনে থেকে জল পড়ার আওয়াজ স্পষ্ট হল; ঝরনার মতো। পাথরের উপর বোধহয় হাতখানেক উঁচু থেকে জল গড়িয়ে পড়ছে, তারই শব্দ। শব্দ শোনা যাচ্ছিল, কিন্তু ঝরনাটা দেখা যাচ্ছিল না। ওটা বোধয় বাঁকটার ও-পাশেই। এদিকে জলের স্রোতও বেশ জোর প্রায় ছয় আঙুল মতো জল একটা হাত পাঁচেক চওড়া ধারায় বয়ে চলেছে।
এখানে ঋজুদা একেবারে স্থাণুর মতো বসে রইল সামনের দিকে চেয়ে। কী জানি, ঐ হনুমানদের হু-হা” শব্দের মধ্যে ঋজুদা কী শুনেছিল- কোন্ ভাষা। কিন্তু তার হাবভাব দেখে আমার মনে হল, বাঘটা ঐ নালার বাঁকেই যে কোনও মুহূর্তে দেখা দিতে পারে।
ঐভাবে কতক্ষণ কেটে গেল মনে নেই। আমার মনে হল, কয়েক ঘণ্টা, কিন্তু আসলে হয়তো পাঁচ মিনিটও নয়।
এখানে কেন বসে আছে, একথা আমি ঋজুদাকে জিজ্ঞেস করব ভাবছি, এমন সময় জলের শব্দ ছাপিয়ে হঠাৎ একটা শব্দ কানে এল। এক মুহূর্ত কান খাড়া করে শুনেই, ভেজা বালিতে হামাগুড়ি দিয়ে নালার বাঁকের দিকে এগোতে লাগল ঋজুদা। শব্দটা আমিও শুনেছিলাম। কুকুরে জল খেলে যেমন চাক্-চাক্-চাক্ শব্দ হয় তেমনই শব্দ, কিন্তু অনেক জোর শব্দ।
শব্দটা তখনও হচ্ছিল। বাঘটা নিশ্চয়ই ঝরনার জল খাচ্ছিল।
বাঁকটা তখনও হাত-দশেক দূরে। ঋজুদা জোরে এগিয়ে চলেছে হামাগুড়ি দেওয়ার মতো করে, রাইফেলটাকে হাতের উপর নিয়ে। আমার বুকের মধ্যে তখন একটা রেলগাড়ি চলতে শুরু করেছে– এত ধধ করছে বুকটা, ঘামে সমস্ত শরীর, মাথার চুল সব ভিজে গেছে। আমার তখন খালি মনে হচ্ছিল, ঋজুদা দেখতে পাওয়ার আগে তার জল-খাওয়া শেষ করে চলে যাবে না তো বাঘটা?
হঠাৎ, একেবারেই হঠাৎ, আমার বুকের স্পন্দন থেমে গেল।
আমার সামনে ঋজুদা বালিতে শুয়ে পড়েছে–প্রোন-পজিশনে দু হাতে রাইফেলটা ধরে নিশানা নিচ্ছে।
ততক্ষণে আমি ঋজুদার পাশে পৌঁছে গেছি। পৌঁছেই যে দৃশ্য দেখলাম তা সারা জীবন চোখে আঁকা থাকবে।
ঝরনাটার উপরে ডানদিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে বাঘটা জল খাচ্ছে। চাঁদের আলোয় তার মাথা, বুক সব দেখা যাচ্ছে, কিন্তু পেছনের দিকটা অন্ধকার। তার প্রকাণ্ড মাথাটা জলের উপর একটা বিরাট পাথর বলে মনে হচ্ছে। আমিও যেই শুয়ে পড়ে বন্দুকটা কাঁধে তুলতে যাব, ঠিক এমনি সময়ে বুক-পকেটে রাখা বুলেটটার সঙ্গে বন্দুকের কুঁদোর ঠোকা লাগতেই খুট করে একটু শব্দ হল। তাতেই বাঘ এক ঝটকায় মাথা তুলে এদিকে তাকাল। বাঘটা কানে-তালা-লাগানো গর্জনের সঙ্গে সঙ্গে শরীরটাকে গুটিয়ে যেন একটা বলের মতো করে ফেলল এবং মুহূর্তের মধ্যে সোজা আমাদের দিকে লাফাল। লাফাল না বলে উড়ে এল, বলা ভাল। আমার কানের পাশে ঋজুদার ফোরফিফটি-ফোরহানড্রেড রাইফেলের আওয়াজে মনে হল বাজ পড়ল। বাঘের গর্জন, হনুমানদের চেঁচামেচি, দাপাদাপি, জঙলের গভীরে অদৃশ্য নানা পাখির চেঁচামেচিতে এবং রাইফেলের গুমগুমানিতে যেন আমি অজ্ঞান হয়ে গেলাম। দেখলাম, আলো-ছায়ায় মেশা একটা অন্ধকারের স্তূপ উড়ে আসছে। আমাদের দিকে শূন্য থেকে, তার সামনে প্রসারিত করা– নখ সমেত প্রকাণ্ড থাবা দুটি। বোধহয় ঘোরের মধ্যেই আমি একই সঙ্গে দুটো ট্রিগার টেনে দিয়েছিলাম বন্দুকের। কিন্তু গুলি লাগল কি না-লাগল কিছু বোঝা গেল না– বাঘটা জলের মধ্যে ঝপাং করে পড়ল, প্রায় আমার নাকের সামনে। আমার মনে হল, থাবাটা একবার তুলে বাঘটা আমার মাথায় এক থাপ্পড় মারল বুঝি। আমি তখনও শুয়েই ছিলাম, দুহাতে বন্দুকটাকে সামনে ধরে।
যেন ঘুমের মধ্যে, স্বপ্নের মধ্যে, যেন অনেক দূর থেকে ঋজুদা আমাকে ডাকল, ‘রুদ্র, এই রুদ্র!
তাকিয়ে দেখলাম, আমার পাশে ঋজুদা বাঘটার ঘাড়ের দিকে রাইফেলের নল ঘুরিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।
আমি উঠে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গেই বাঘটাও যেন একবার উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল, সারা শরীর নড়ে উঠল, জল ছপছপ করে উঠল, ডন দেবার মতো উঠে দাঁড়াতে গেল বাঘটা। ঋজুদা রাইফেলটা কোমরে ধরা অবস্থাতেই বাঁ-ব্যারেল থেকে আবার গুলি করল। বাঘটার মাথাটা ঝপাং করে জলে পড়ল।
একটাও কথা না বলে ঋজুদা ঝরনার কাছ দিয়ে নালা পেরিয়ে বাইরের উপত্যাকায় এল। এসে ফাঁকা জায়গা দেখে একটা বড় পাথরের উপরে বসে পকেট থেকে পাইপটা বের করে ধরাল। বলল, গাঁয়ের শিকারীর নিশানা ফসকে গিয়েছিল। তার গুলি সত্যিই বাঘের পায়ে লেগে থাকলে ব্যাপারটা এত সহজে শেষ হত না। দূরে দেখা গেল– ঝাঁকড়া পিপুল গাছের দিক থেকে একটা লোক আমাদের দিকে জ্যোৎস্নায় ভেসে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে আসছে। মাহাতো।
হঠাৎ ঋজুদা যেন কেমন উদাস হয়ে গেল।
পিউ-কাঁহা পাখিটা অনেকক্ষণ চুপচাপ থাকার পর আবার ডাকতে লাগল দূর থেকে। বাঘ মরে গেছে– এ-খবরে আনন্দ কী দুঃখ প্রকাশ করল জানি না, কিন্তু চতুর্দিকের বন-পাহাড়ে আবার নানারকম পশুপাখির ডাক শোনা যেতে লাগল।
আমি শুধোলাম, ঋজুদা, ছেলেটা?
ঋজুদা পাইপের ধোঁয়া ছেড়ে বলল, কিছু করার নেই। ওর বাবা-দাদারা আসবে যাদের আপনজন, তারাই নিয়ে যাবে। কী-ই বা করার আছে আমাদের?
আমি শুধোলাম, কোথায় আছে?
ঋজুদা বলল, এমনভাবে বলল, যেন নিজে দেখেছে, ঐ ঝরনার ওপাশে, বেশ কিছুটা ও-পাশে, নালার মধ্যেই পড়ে আছে।
আমিও পাথরটার উপরে বসে পড়ে খুশি গলায় বললাম, যাক্, বাঘটাকে মেরেছ ভালই হয়েছে। বদমাইস বাঘ।
ঋজুদা শুকনো হাসি হাসল। বলল, আহা, কী দারুণ বাঘটা! বেচারা!
তারপরই বলল, উপায় ছিল না বলেই হয়তো ও ছেলেটাকে মেরেছিল। জন্তু-জানোয়ারদের ভালবাসিস, বুঝলি, রুদ্র। মানুষকে মানুষ তো ভালবাসেই। কিন্তু ওদের ভালবাসতে পারে, ভালবাসতে জানে, খুবই কম। মানুষ।
.
ঋজুদার সঙ্গে সিমলিপালে
ভর-দুপুর। টাইগার প্রোজেক্টের ডিরেকটর সাঙ্খলা সাহেব, যশীপুরের খৈরী-খ্যাত চৌধুরী সাহেব ও আরও একজন দক্ষিণ ভারতীয় একোলজিস্ট ওড়িশার ন্যাশনাল পার্ক সিমলিপালের পাহাড়ের মধ্যে বড়াকামড়ার ছোট বাংলোর বারান্দায় বসে লাঞ্চ খাচ্ছিলেন।
ঋজুদা তাঁদের টা-টা করে বেরিয়ে পড়লেন। জেনাবিলের দিকে। জীপের মুখটা ঘুরল, কিন্তু ট্রেলারটা ঘুরল না। ট্রেলারগুলো বড়ই বেয়াদব হয়। জীপ ডাইনে ঘুরলে বাঁয়ে ঘঘারে, বাঁয়ে ঘুরলে ডাইনে। আমি আর বাচ্চু হ্যাট হ্যাট করে হালের বলদ তাড়াবার মতো করে, নেমে পড়ে হাত দিয়ে পা দিয়ে ট্রেলারকে বাধ্য করালাম জীপের কথা শুনতে।
তারপর বড়াকামড়ার বাংলোর গড়ের উপরের সাঁকো পেরিয়ে এসে জীপ মুখ ঘোরাল ডানদিকে।
এই সিমলিপালের জঙ্গলে ঋজুদা একা আসেননি। সঙ্গে ঋজুদার জঙ্গলতুতো দাদা কানুদা এবং তার জঙ্গল-পাগল স্ত্রী ও শালী, খুকুদি ও মণিদি। সঙ্গে দিদি ও জামাইবাবু-অন্তপ্রাণ বাচ্চু।
এত লোক সঙ্গে থাকায় আমি ঋজুদাকে মোটেই একা পাচ্ছি না। আমাকে এইসব নতুন লোকেরা মোটেই পাত্তাও দিচ্ছেন না। মনমরা হয়ে ট্রেলারে মালপত্রের উপরে বসে আছি। “খিদমদগার” বাচ্চু এবং ‘ইউসলেস’ আমার জায়গা ডাঁই-করা মালপত্র-ভরা ট্রেলারের উপর।
পাহাড়ী রাস্তা। জীপ যখন উত্রাইয়ে নামে, তখন আমরা এ-ওর ঘাড়ের উপর পড়ে একেবারে ট্রেলারের সামনে এসে পড়ে জীপের চাকার তলায় যাই আর কী! আবার জীপ যেই চড়াইয়ে ওঠে, তখন আবার সড়াৎ করে ট্রেলারের পেছনে চলে গিয়ে গড়িয়ে চিৎপটাং হয়ে পড়ো-পড়ো, পাথরে। অনেক পাপ করলে মানুষকে জীপের ট্রেলারে চড়তে হয়।
বড়াকামড়ার বাংলোর সামনেই শবরদের একটা বস্তি। সার সার খড়ের ঘর, নদীর ওপারে ঝুঁকে পড়া পাহাড়ের গায়ে। বর্ষার বাঁক-নেওয়া ভরন্ত পাহাড়ী নদীর পাশে, নরম সবুজ প্রান্তরের উপর। দূর থেকে যেন পাণ্ডবদের বনবাসের পর্ণকুটির বলেই মনে হয়। এখন চৈত্রের শেষ। লক্ষ লক্ষ শালগাছে মঞ্জরী এসেছে। মেঘলা আকাশ। মেঘলা আকাশের পটভূমিতে পুষ্পভারাবনত শালগাছগুলিকে যে কী সুন্দর দেখাচ্ছে, তা বোঝাবার মত ভাষা আমার নেই। কাল সকাল থেকে একটানা বৃষ্টি হচ্ছিল। আজ ভোরে থেমে গেছে। বৃষ্টির পর লাল মাটির কাঁচা রাস্তা, পুষ্পশোভিত কচি কলাপাতা রঙা শালবন, ওয়াশের কাজের মতো পাহাড়শ্রেণীর নয়ানাভিরাম দৃশ্য দেখে ট্রেলারে চড়ে জঙ্গলে ঘোরার মারাত্মক ঝুঁকি ও শারীরিক কষ্টও যেন ভুলে গেলাম।
হঠাৎ মণিদি বললেন, হাতি, হাতি!
কানুদা বললেন, দিন-দুপুরে হাতি না ছাই। স্বপ্ন দেখছিস!
ওমা! চেয়ে দেখি, সত্যিই হাতি। দুটো প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হাতি ঝাঁটি-জঙ্গলে ভরা ছোট টিলা পেরিয়ে ওপারের উঁচু টিলাতে যাচ্ছে হেলতে-হেলতে দুলতে-দুলতে আর তাদের পায়ে পায়ে একটা গাবলুগুবলু বাচ্চা। গোলগাল, গোবর-গণেশ, একহাত উঁড়টাকে নাড়াতে নাড়াতে চলেছে।
বাচ্চু একদৃষ্টে তাকিয়েছিল, আমরা সকলেই। হঠাৎ বাচ্চু বলল, রুদ্র, হাতির মাংস কখনও খেয়েছ? বোধ হয় পাঁঠার চেয়েও নরম হবে। দৌড়ে গিয়ে ধরি?
বলেই, কারও পারমিশানের অপেক্ষা না করে ট্রেলার থেকে এক লাফে নেমে হাতিদের দিকে দৌড় লাগাল ও।
জীপের মধ্যে সকলে সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল, কী হল? কী হল?
কী হল, তা জানতে এতটুকু উৎসাহ না দেখিয়ে কানুদা উৎসারিত কণ্ঠে বললেন, আমার ক্যামেরা! ক্যামেরা! বলেই সামনের সীটে বসে পেছন দিকে জোরে গল-খেলা তাগড়া হাত ছুঁড়লেন।
হাতটা এসে লাগল মণিদির নাকে।
মণিদি বললেন, উঁ বাঁবাঁ-রে।
ঋজুদা চুপ করে ছিলেন, পাইপের ভুড়ক ভুড়ক আওয়াজ হচ্ছিল।
কানুদা শালীকে ধমকে বললেন, মণি, ক্যামেরা কোথায়? শিগগির দাও। এখন ন্যাকামি করো না।
ন্যাঁকামি নাঁ। নেঁই। বলেই মণিদি নাকী সুরে কেঁদে উঠলেন।
ঠিক সেই সময় কানুদা বললেন, নেই মানে? ইয়ার্কি পেয়েছ?
আমি ঘোড়ার পিঠে বসার মতো করে ট্রেলারের দুদিকে দুপা ছড়িয়ে দিয়ে বসে বাচ্চুর কার্যকলাপ রিলে করছিলাম।
বললাম, এইবার সেরেছে! সর্বনাশ।
সকলে চেয়ে দেখলেন, বড় হাতিটা বাচ্চুর দিকে ফিরে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু বাচ্চু নির্বিকার। ও হাতির বাচ্চার রোস্ট খাবেই।
কানুদা আবার বললেন, মণি, ক্যামেরা!
মণিদি বললেন, ডাঁলমুঁটের ঠোঁঙার মঁধ্যে রেঁখেছিলাম। ডাঁলমুটের ঠোঁঙাটা কাঁঠের বাঁক্সে। কাঁঠের বাঁক্সটা ট্রেঁলারে।
কানুদা একটা চাপা কিন্তু তীব্র ধমক দিলেন মণিদিকে। সংক্ষিপ্তসার– ইডিয়ট।
মণিদি ভ্যাঁ-অ্যা করে কেঁদে দিলেন।
ওদিকে হাতি ডেকে উঠল, প্যাঁ-অ্যা-অ্যা-অ্যা। ডেকেই, শুঁড় তুলে ডান পায়ে শূন্যে ফুটবলে লাথি মেরে এগিয়ে এল। শর্টসপরা ও হাওয়াইয়ান চপ্পল-পরা বা দৌড়ে পালিয়ে আসতে গিয়ে একটা হোঁচট খেয়ে পড়ল ধ্বপাস করে। তারপর উঠে দৌড়ে এসেই দূর থেকে লং-জাম্প দিয়ে সোজা এসে ট্রেলারে পড়ল। প্রায় আমার ঘাড়ে। ও-ও ধ্বপ্ করে পড়ল, কানুদাও বললেন, গেল!
বাচ্চু লজ্জিত হয়ে পেছনে না তাকিয়েই বলল, কী গেল? হাতি? চলে গেল?
তারপর সঙ্গে সঙ্গে বলল, আমার একপাটি চপ্পলও!
মণিদি বললেন, নাঁ-আঁ-আঁ। বোঁধ হঁয় ভেঁঙে গেঁল। কাঁনুদার ক্যাঁমেঁরা, উঁ-হুঁ-হুঁ-হুঁ–।
কানুদা আবার বললেন, ইডিয়ট।
ঋজুদা জীপটা জোরে চালিয়ে দিয়ে বলল, কে? বাচ্চু, না মণিদি?
দুজনেই। কানুদা রেগে বললেন।
এরপর জীপের আরোহীরা নিস্তব্ধ। শুধু মাঝে মাঝে মণিদির নাক টানার শব্দ।
কিন্তু রাস্তার দৃশ্যের তুলনা নেই। কানুদার মতো ঋজুদা ক্যামেরাতে বিশ্বাস করে না। চোখের টু-পয়েন্ট লেন্সে এইসব নিসর্গ-ছবি তুলে নিয়ে মস্তিষ্কের মধ্যের অন্ধকার ল্যাবরেটরিতে লুকিয়ে রেখে দেয় অবচেতনের ভাঁড়ারে। যখন যেমন, দরকার পড়ে, তখন তেমন সেই সব মুহূর্তের, দৃশ্যের, পরিবেশের শব্দ, গন্ধ, রূপের সামগ্রিক চেহারাটা তার কলমের মুখ থেকে সাদা পাতায় ছড়িয়ে পড়ে। মানুষের মস্তিষ্ক যা পারে, যা ধরে রাখে, পৃথিবীর কোনও ক্যামেরা বা টেপ-রেকডারই তা পারে না। মানুষ যেদিন গন্ধ-ধরা যন্ত্রও বের করবে সেদিনও পারবে না।
পথের বাঁকে হঠাৎ হাওয়ায় ভেসে-আসা বুনো চাঁপার গন্ধ বা মেঘলা আকাশের মৃদু-মৃদু হাওয়ায় আলতো হয়ে ভাসতে-থাকা শালফুলের গন্ধকে কি কোনও যন্ত্র ধরতে পারে?
আমরা ময়ূরভঞ্জের রাজার শিকারের বাংলো ভঞ্জবাসার পথ ছেড়ে এসেছি। পথটা বড়াকামড়া বাংলো থেকে নদী পেরিয়ে লাল মাটির মালিমা মেখে ছুটে গেছে সবুজ জঙ্গলের গভীরে। গতকাল আমরা রাজার বাড়ি চাহালাতে ছিলাম। চাহালা নামটার একটা ইতিহাস আছে। এখানে রাজা প্রত্যেকবার শিকারে আসতেন। একবার হাঁকা শিকারের সময় রাজা এবং তাঁর বন্ধুবান্ধবেরা অনেক জানোয়ার মারলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হল শিলাবৃষ্টি। সে কী। শিলাবৃষ্টি! রাজার ক’জন বন্ধু মারা গেলেন, মারা গেল অনেক হাঁকাওয়ালা। রাজাও নাকি আহত হয়েছিলেন। লোকে বলতে লাগল যে, ভগবানের আসন টলে গেল। মরণোন্মুখ ও আহত পশুপাখির কান্নায় ও চিৎকারে ভগবানের আসন টলে গেছিল সেদিন। সেই থেকে নাম চাহালা। সেই দিন থেকে চাহালাতে শিকার বন্ধ। এমনকী, গাছ পর্যন্ত কাটা হত না রাজার আমলে। এখনও অনেক বনবিভাগের অফিসার সেকথা মেনে চলেন। বাংলোর হাতায় একটা পিয়াশাল গাছ আছে কুয়োয় যাওয়ার পথে, তার চারদিকে কাঁটাতার দিয়ে ঘিরে রেখেছেন রেঞ্জার মিত্রবাবু। পাছে ভুল করে গাছটার কেউ ক্ষতি করে।
এখানে প্রকৃতির পুত্র কন্যাদের উপর বিন্দুমাত্র অন্যায় হলে আবারও ভগবানের আমন টলতে পারে। সকলেই এই ভয় বুকে নিয়ে বাঁচেন ওখানে।
চাহালা বেশ উঁচু। গরমের দিনেও ঠাণ্ডা। অনেকগুলো ইউক্যালিপটাস গাছ আছে হাতার মধ্যে, বৃত্তাকারে লাগানো। বসন্ত-সকালের সোনার রোদ যখন ইউক্যালিপটাসের মসৃণ পাতায় চমকাতে থাকে, সুনীল আকাশের নীচে তখন নীলকণ্ঠ পাখি বুকের মধ্যে চমক তুলে ডেকে ডেকে ওড়ে। টিয়ার ঝাঁক শিহর তুলে একদল ছোট্ট সবুজ জেট-প্লেনের মতো ছুটে যায় নক্ষত্র জয়ের জন্য। নীলোৎপল আকাশে।
একটা পথ বাংলোর ডাইনে দিয়ে বেরিয়ে গেছে হদিয়ার দিকে; বারো কিলোমিটার। অন্য পথ, কাইরাকচার দিকে। এই দুজায়গায়ই বনবিভাগের ছোট্ট মাটির ঘর আছে। খড়ে-ছাওয়া বাংলো। তার চারপাশে হাতি যাতে না আসতে পারে, সেজন্যে গভীর গড় কাটা। ছোট্ট নিকোনো মাটির উঠোন। ছোট্ট বারান্দা। স্বপ্নে দেখা ছবির মতো। পাশেই ঝরনা। বড় বড় গাছ ঝুঁকে পড়েছে চারধার থেকে। মাটির উঠোনে টুপটাপ পাতা পড়ে ঝরে ঝরে। নির্জন দুপুরে কাঁচাপোকা ওড়ে বুঁ–বুঁবুঁ–বুঁ-ই-ই-ই আওয়াজ করে। জংলী হাইবিস্কাস-এর সরু ডালে বসে নানারঙা মৌটুসী পাখি শিস দেয়। দূর থেকে হাতির দলের বৃংহণ ভেসে আসে, কোটরা হরিণ ডেকে ওঠে ব্বা, ব্বা, ব্বা করে। সেই উদাত্ত আওয়াজ অনুরণিত হয় পাহাড়ে পাহাড়ে, বনে বনে। উঁচু গাছের ডাল থেকে অর্কিড় দোলে মন্থর খেয়ালী হাওয়ায়। গন্ধ ওড়ে।
চাহালা থেকে আরও একটা রাস্তা গেছে ন-আনা হয়ে, বড়াই পানি জলপ্রপাতের পাশ দিয়ে। যে প্রপাত থেকে বুড়াবালাম্ নদীর সৃষ্টি। তারপর পৌঁছেছে গিয়ে ধুরুচম্পাতে। কী দারুণ নামটা, না? ধুরুচম্পা। এখানে আরও সব সুন্দর সুন্দর নামের জায়গা আছে। যেমন বাছুরিচরা। ধুরুচম্পাতে পৌঁছলে মনে হয় খাসীয়া পাহাড়ের কোনও নিভৃত জায়গায় এসেছি, অথবা কুমায়ুনের চিড় আর চিড়। শুধু চিড়ের বন। ময়ূরভঞ্জের রাজা বহু বহু বছর আগে এই উঁচু মালভূমিতে পাইন গাছ এনে লাগিয়েছিলেন। ঘন গহন পাইন বন। লোক নেই, জন নেই, দোকান নেই, শুধু বন আর বন। হাওয়া ওঠে যখন পাইনের বনে, তখন এমন এক মর্মরধ্বনি ওঠে যে কী বলব! পাইনের গন্ধ ভাসে হাওয়ায়। চিড়ের ফলগুলো ঝরা চিড়পাতার মখমল গালচের উপরে নিঃশব্দে গড়িয়ে যায়। গা শিরশির করে ভাললাগায়। তার সঙ্গে মিশে যায় কত না নাম-জামা এবং না জানা ফুলের গন্ধ।
প্রত্যেক জঙ্গলের গায়েরই একটা নিজস্ব গন্ধ আছে। প্রত্যেক মানুষের গায়ের গন্ধের মতো। গন্ধ ঋতুতে ঋতুতে বদলায়। যেমন বদলায় শব্দ; যেমন বদলায় রূপ। চৈত্রের হাওয়ায় বনের বুকে যে কথা জাগে, সে কথার সঙ্গে শ্রাবণের কথা বা মাঘের কথার কত তফাত! সে রূপেরই বা কত তফাত! যার চোখ আছে, সে দেখে; যার কান আছে, সেই শোনে; যার হৃদয় আছে, সেই শুধু হৃদয় দিয়ে তা উপলব্ধি করে।
অনেকেই জঙ্গলে যান, হৈ-হৈ করেন, পিকনিক করে চলে আসেন, কিন্তু জঙ্গল তাঁদের জন্যে নয়। পিকনিক করার অনেক জায়গা আছে। জঙ্গলে গেলে নিজেরা কথা না বলে জঙ্গলের কী বলার আছে তা শুনতে হয়।
ন-আনা জায়গার নামটাও ভারী মজার, তাই না? এর একটা ইতিহাস আছে। রাজার খাজনা ছিল এখানে ন-আনা। তাই জায়গাটার নাম ন-আনা।
ন-আনা জায়গাটাও ভারী সুন্দর। ধুরুচম্পা বা জেনাবিলের মতো এখানকার বাংলো কাঠের দোতলা নয়। পাকা বাংলো। চাহালাতেও। বাংলোটা একটা টিলার মাথায় বহুদূর চোখ যায়। অনেকখানি জায়গা জঙ্গল কেটে ফাঁকা করা আছে। পাহাড়ী নদী গেছে এঁকেবেঁকে। ধু-ধু উদোম টাঁড় কিন্তু রুক্ষ নয়।
এই চৈত্ৰশেষের বৃষ্টিতেও চারিদিক সতেজ সবুজ দেখাচ্ছে। আমরা যখন ন-আনায় যাচ্ছিলাম, তখন আমাদের সঙ্গে একজন গো দম্পতির দেখা হয়ে গেছিল। তীর-ধনুক হাতে নিয়ে চলেছিল কালো ছিপছিপে বাবরি চুলের ছেলেটি আর হলুদ রঙে ছোপানো শাড়ি পরা মেয়েটি। মেঘলা আকাশের নীচে।
কানুদাকে শুধোলেন ঋজুদা, রাতে কোথায় থাকা হবে?
জেনাবিলে। কানুদা বললেন।
বাচ্চু বলল, এই সেরেছে!
আমি বললাম, কেন? অসুবিধা কিসের?
ও বলল, না। পরে বলব।
দেখতে দেখতে আমরা দেও নদীতে এসে পড়লাম। বড় বড় মাছ আছে। নদীটাতে। একটা দহের মতো হয়েছে। বর্ষার লাল মাটি-ধোওয়া ঘোলা জল ভরে রয়েছে। কানায় কানায়।
হঠাৎ বাচ্চু আমাকে বলল, কানায় কানায় ইংরিজী কী? আমি অনেক ভাবলাম। তারপর বললাম, জানি না।
কানুদা বললেন, মণি, নাক কেমন?
মণিদি বললেন, ভাঁল। একটু রক্ত বেরিয়েছে।
খুকুদি বললেন, তোর একটুতেই বাড়াবাড়ি।
মণিদি বললেন, হুঁ, তোঁর নিজেঁর বঁর কিঁনা, হুঁ..!
ঋজুদা বললেন, ওঁ মণিপদ্মে হুম্।
কানুদা বললেন, বাঁদিকে নয়; ডানদিকে।
ভুল করে ঋজুদা বাঁদিকে চলে যাচ্ছিল। কানুদা স্টীয়ারিং ডানদিকে ঘুরিয়ে দিলেন।
দেও নদী পেরিয়ে আমরা দেবস্থলীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। জনমানব নেই, লোকালয় নেই– জঙ্গল আর জঙ্গল। মাইলের পর মাইল থমথমে নিস্তব্ধতা। দেবস্থলীতে একটা ছোট্ট খড়ের ঘর– চারধারে গড় কাটা, হাতির জন্যে। টাইগার প্রোজেক্টের বাংলো। কোনও ফরেস্ট গার্ড থাকেন বোধ হয়। এখন কাউকে দেখলাম না।
বাচ্চু বলল, রুদ্র, তুই কখনও বাঘের মাংস খেয়েছিস?
আমি বললাম, না। তবে প্রায় সব জানোয়ারেরই খেয়েছি, এক গাধা। ছাড়া।
বাচ্চু বলল, কাক কখনও কাকের মাংস খায়?
আমি বললাম, কী বললি?
বলতেই সামনে থেকে ওঁরা সকলে হেসে উঠলেন।
আমার কান লাল হয়ে উঠল। এই জন্যেই অল্প-চেনা লোকদের সঙ্গে আসতেই চাই না কোথাও। ঋজুদাটা আর মেশার লোক পেল না। ভাল লাগে না।
দূর থেকে পাহাড়ের ওপর থেকে নীচের সমান প্রান্তরে ছবির মতো। জেনাবিল গ্রামটা চোখে পড়ল। একটা হাতির কঙ্কাল পড়ে আছে। দুটো হাতি নাকি লড়াই করেছিল এখানে, সিমলিপালের রিপোর্টার কানুদা বললেন।
মণিদি বললেন, নাঁ। লড়াই না।
আদর। বাচ্চু বলল, বাঁদর।
কানুদা বললেন, কোথায়?
ঋজুদা বললেন, ট্রেলারে।
অনেকগুলো বাঁদর পথ পেরিয়ে এপাশ থেকে ওপাশে গেল।
কানুদা বললেন, পারফেক্ট হেলথ।
জেনাবিলের কাঠের বাংলোটা হাতিরা ধাক্কাধাক্কি করে ফেলে দেওয়ার উপক্রম করেছিল। বাংলোটা হেলে গেছে। বড় বড় কাঠের গুঁড়িগুলোকে সোজা করে বসাবার জন্যে এবং পাশে পাশে ঠেকনো দেওয়ার জন্যে বিরাট বিরাট গর্ত খোঁড়া হয়েছে। বাংলো পুরোপুরি সারাবার আগে বহু লোকের যে পা ভাঙবে, মাথা ফাটবে এই গর্তে পড়ে, তাতে সন্দেহ নেই।
বাংলোটার সব ভাল। কিন্তু বাথরুম নেই। কোনও ফার্নিচারও নেই। একটা চেয়ার পর্যন্ত নয়। মাটিতে শোওয়া, মাটিতে বসা। নীচে গার্ডের ঘরে রান্না করা। বেশ দূরের ঝরনাতে চান, হাত-মুখ ধোওয়া। সিমলিপালের বেশির ভাগ বাংলোতেই রান্নাবান্না সব নিজেদেরই করতে হয়। সেজন্যে অসুবিধা নেই। কিন্তু বাঘ-হাতির জঙ্গলে রাত-বিরেতে প্রাকৃতিক আহ্বানে সাড়া দিতে জঙ্গলে যাওয়া একটু অসুবিধের!
বাংলোয় পৌঁছে খুকুদি বললেন, মণি, তাড়াতাড়ি স্টোভটা বের কর। চা বানাই। তারপর খিচুড়ির বন্দোবস্ত করে বেরিয়ে পড়র এক চক্কর। সন্ধের মুখে-মুখেই তো জানোয়ার বেরোয়। তারপরই আবার বললেন, মুগের ডাল আছে? ঋজুদা এতক্ষণ কোনও কথা বলেনি। এখন জীপ থেকে নেমে গার্ডের ঘরের দাওয়ায় পা ছড়িয়ে বসে পাইপে নতুন করে তামাক ভরতে ভরতে বলল, খুকুদি, তাড়াতাড়ি চা।
চা খেয়ে খেয়ে খুকুদি ডিসপেপটিক। ঋজুদার মতো চা-ভক্ত তোক পেয়ে খুশি।
মণিদি স্টোভ বের করলেন। খুকুদি বললেন, মুগের ডাল দিয়ে খিচুড়িটা ভাল করে রাঁধতে হবে রাতে। সকালবেলা ভাল হয়নি।
বাচ্চু আতঙ্কিত গলায় বলল, আবারও খিচুড়ি?
খুকুদি বললেন, না তো কী! এই জঙ্গলে তোমার জন্যে বিরিয়ানি পাব কোত্থেকে?
বাচ্চু বলল, না, তা বলছি না। মানে, একটু অসুবিধা ছিল। তারপরই বলল, ওষুধের বাক্সে কি কিছু আছে?
ও! তোর বুঝি পেট খারাপ হয়েছে? খুকুদি বললেন।
বাচ্চু বলল, দশদিন তো হল এবেলা খিচুড়ি, ওবেলা খিচুড়ি। তারপর চারধারের জঙ্গলে চোখ বুলিয়ে নিয়েই বলল, আমি নেই। যা খেয়েছি সকালে, অনেক খেয়েছি। আর খাওয়া-দাওয়ার মধ্যে নেই।
আমি বললাম, ভয় কিসের? যেদিকে তাকাবি, সেদিকেই তো উদার, উন্মুক্ত।
বাচ্চু রেগে বলল, তুই যা না, যতবার খুশি।
মণিদি বললেন, বাঁদর।
আমি ও বাচ্চু দুজনেই একসঙ্গে তাকালাম। তারপর বুঝলাম যে আমরা নই।
একটা বড় বাঁদর গার্ডের ঘরের পাশের গাছে বসে আছে। তাড়াতাড়ি করে চা খেয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম একটা বড় চক্কর ঘুরে আসবার জন্যে জিনিসপত্র নামিয়ে রেখে জীপের ট্রেলার খুলে রেখে। জেনাবিল থেকে ধুপ্রুচম্পা যাওয়ার এই স্বল্প ব্যবহৃত পথটাতে যে কত জীবজন্তু দেখেছিলাম আমরা আসার সময়, তা বলার নয়; দিনের বেলা দলে দলে হাতি, ময়ুর, হিষালয়ান স্কুইরেল, বাঁদর, বার্কিং ডিয়ার।
প্রায় পাঁচ কিলোমিটার মতো গেছি, একদল বুনো কুকুর লাফাতে লাফাতে রাস্তা পেরুল। মুখ দিয়ে অদ্ভুত একটা আওয়াজ করছিল ওরা।
ঋজুদা বলল, বুনো কুকুর এসেছে যখন, তখন এখানে এখন কিছু দেখা যাবে না।
কানুদা বললেন, চলোই না একটু ভিতরে।
আসন্ন সন্ধ্যার আধো-অন্ধকারে ময়ূর ডাকছে, মুরগী ডাকছে, বাঁদর হুপ-হুপ-হুপ-হুপ করে উঠছে গভীর জঙ্গল থেকে। হাতির দল দূর দিয়ে দিনের শেষে ঘুমের দেশে চলেছে সারি বেঁধে, গায়ে লাল মাটি মেখে। মনে হয় স্বপ্ন। বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না সত্যি বলে।
হঠাৎ ঋজুদা জীপটা হল্ট করিয়ে দিয়ে বলল, মামা!
বাচ্চু বলল, কার মামা?
খুকুদির লম্বা হাতটা জীপের পেছনের আধো-অন্ধকারে এসে বাচ্চুর কানে আঠা হয়ে সেঁটে গেল। খুকুদির হাতটা বাচ্চুর কানে পড়তেই বাচ্চুর ও আমার চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেল।
পথের ডানদিকে খাদ– বাঁদিকে পাহাড়। সূর্য ডুবে এসেছে। মামা আসছে। গোঁফে তাড়া দিয়ে সোজা হেঁটে জীপের একেবারে মুখোমুখি।
সকলে স্ট্যাচু হয়ে গেছে জীপের মধ্যে। শুধু ঋজুদার পাইপের শব্দ ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই।
প্রকাণ্ড বড় চিতা। চমৎকার চিক্কণ চেহারা। গোঁফ দিয়ে জেল্লা বেরুচ্ছে। এ-জঙ্গলে মানুষ বোধহয় একেবারেই আসে না, নইলে চিতার এমন ব্যবহার আমি কখনও দেখিনি।
জীপের থেকে হাত কুড়ি দূরে চিতাটা সোজা বুক চিতিয়ে দাঁড়াল। দিনের শেষ আলোর ফালি এসে পড়ল ওর গায়ে। সে এক দারুণ সৌন্দর্য ও স্তব্ধতার মুহূর্ত।
সেই নৈঃশব্দ্য ভঙ্গ করে হঠাৎ কানুদা উত্তেজিত হয়ে বললেন, মণি, ক্যামেরা! বলেই সকালের মতো আবারও হাত ছুঁড়লেন।
‘মা-গোঁ-ও’ বলে মণিদি জীপের মধ্যেই বসে পড়লেন। চিতাটা ভীষণ ভয় পেয়ে চমকে উঠে এক লাফে খাদের দিকে দৌড়ে গেল। তারপর কী করে নামল খাদ বেয়ে, তা সে চিতাই জানে। ডিগবাজি খেয়ে নিশ্চয়ই ওরও নাক ভাঙল।
খুকুদি বললেন, এটা বাড়াবাড়ি কানু, তোমার ক্যামেরা তুমি ঠিক করে রাখতে পারো না? মেয়েটার নাক দিয়ে এখনও রক্ত ঝরছে, তার ওপর আবার আঘাত?
কানুদা বললেন, ক্যামেরা কোথায়?
কাঁজুবাদামের টিনে। মণিদি কোঁকাতে কোঁকাতে বললেন।
কানুদা চিতাবাঘটা লাফানোর আগে যেন ধনুকের মতো বেঁকে গেছিল, তেমনি রাগে বেঁকে গিয়ে বললেন, দেয়ার এ লিমিট। ডালমুটের ঠোঙা থেকে বের করে কাজুবাদামের টিনে–ক্যামেরা?
মণিদি জামাইবাবুকে খুব ভালবাসেন।
বললেন, তুঁমিই না বঁলেছিলে বৃষ্টিতে লেন্সে ফাঙ্গাঁস পড়ে যাবে? আমি তাঁই যত্ন কঁরে-এ-এ-এ। উঃ-হুঁ-হুঁ–।
ঋজুদা জীপ থেকে নেমে বললেন, এইরকম কোনও জায়গাতেই শূর্পণখার নাক কাটা গেছিল। এখানে প্রত্যেকের নাক সাবধান রাখা উচিত। বলে রুমাল বের করে নিজের নাক মুছল।
খুকুদি বললেন, বাচ্চু, মণির নাকে ওয়াটার বট থেকে একটু দল দে তো।
কোথায় বাচ্চু?
তাকিয়ে দেখি বাচ্চু নেই। কখন যে হাওয়া হয়েছে, কেউই লক্ষ করিনি।
বাঘও ডানদিকে খাদে লাফিয়েছে, বাছুও বাঘকে ডোন্টকেয়ার করে বাঁদিকে পাহাড়ে চড়েছে। ও বলেইছিল যে, ওর একটু অসুবিধা আছে। কিন্তু বাঘের চেয়েও যে বেশি ভয়াবহ কিছু আছে, একথাটা সেবারেই প্রথম জানলাম। বাঘ তো বাঘই; কিন্তু খিচুড়ি-ঘোগ।
.
হলঙ
বাগডোগরা এয়ারপোর্টে যখন বোয়িং প্লেনটা নামল তখন ভরদুপুর।
একজন কালো মতন ভদ্রলোক, চশমা-পরা, প্লাস্টার করা ডান হাত স্লিংয়ে ঝোলানো, এগিয়ে এসে ঋজুদাকে নমস্কার করলেন।
ঋজুদা বলল, কী বিকাশ? কেমন আছ? যাচ্ছ তো হলঙে আমাদের সঙ্গে?
ভদ্রলোক বললেন, কী করে যাই? দেখতেই পাচ্ছেন। গাড়ি অ্যাকসিডেন্টে ডান হাত ভেঙেছি। তাছাড়া কাল ভোরেই কলকাতা যাব, বিশেষ কাজ আছে।
তারপর বললেন, আপনি একা জীপ নিয়ে যেতে পারবেন তো? ড্রাইভার ছাড়া আমি যে অচল।
ঋজুদা বললেন, না, না, ঠিক আছে। একা যেতে পারব না কেন? তাছাড়া একা তো নই, সঙ্গে আমার চেলা, এই রুদ্রচন্দ্র আছে। কোনওই অসুবিধে নেই।
আমি জীপের পেছনে উঁকি দিয়ে দেখলাম, ছ’টা মুরগি কঁক কঁক করছে। পাশে একটা বড় প্যাকিং বাক্স। তাতে চাল, ডাল, তরকারি, ফল, তেল ঘি– এই সব।
বিকাশবাবু বললেন, সবই দিয়ে দিয়েছি, আপনার কোনওই অসুবিধে হবে না। ওখানে তো পাওয়া যায় না কিছু। এবার দেরি না করে বেরিয়ে পড়ন। অনেকখানি পথ।
ঋজুদা স্টীয়ারিং-এ বসল। আমি গিয়ে পাশে বসলাম।
তারপর বিকাশবাবুর সঙ্গে কী সব কথাবার্তা বলে জীপ স্টার্ট করল ঋজুদা।
চলি, বলে ডান হাতটা বিকাশবাবুর দিকে তুলে জীপের অ্যাকসিলেটরে চাপ দিল। তারপর জীপ ছুটে চলল।
ঋজুদা বলল, দূর, এই জীপ ভাল না।
আমি শুধোলাম, কেন?
এটা বড্ড ভাল। জীপের স্টীয়ারিং কমপক্ষে আড়াই-তিন পাক ফল না হলে কি চালিয়ে আরাম! বাঁই বাঁই করে তিন পাক স্টীয়ারিং ঘুরে গেলে তবে চাকা একটু সরবে, সেই-ই তো মজা।
দেখতে দেখতে আমরা এয়ারপোর্টের এলাকা পেরিয়ে এসে ফাঁকায় পড়লাম। দার্জিলিং-এ যাওয়ার রাস্তা বাঁদিকে ফেলে বাইপাস দিয়ে এসে আমরা সেভক রোড ধরলাম।
বেশ ঠাণ্ডা এখন, এই দুপুরেও। হাওয়া লাগছে চোখে-মুখে। মাথার উপর ঝকঝকে নীল আকাশ– দুপাশে ঘন শালের জঙ্গল, সেগুনের প্ল্যানটেশান মধ্যে দিয়ে আর্মির বানানো চওড়া কালো অ্যাসফল্টের রাস্তা সোজা চলে গেছে। তিস্তা অবধি। তিস্তা পেরিয়ে সেভক ব্রীজ পেরিয়ে ডুয়ার্সে যাওয়ার পথ, আর সোজা গেলে, খরস্রোতা তিস্তার গায়ে গায়ে কালিম্পং যাওয়ার রাস্তা।
বেশ জোরেই জীপ চালাচ্ছিল ঋজুদা। জীপের এঞ্জিনটা মাঝে মাঝে স্পীড কমে গেলেই, সে যে তত ভাল ছেলে নয়, যতটা ঋজুদা ভেবেছিল, তা প্রমাণ করার জন্যে মাথা নাড়ছিল পাগলের মতো। সঙ্গে সঙ্গে জোরে একটা লাথি মারছিল ঋজুদা ক্লাচে। অমনি আবার সে ভাল ছেলে হয়ে যাচ্ছিল। সেভকে এসে বিখ্যাত করোনেশন ব্রীজ পেরোলাম আমরা। ব্রীজের পর বেশ কিছুটা পথ আঁকাবাঁকা পাহাড়ী পথ, তারপর আবার সটান, সোজা, আদিগন্ত।
ওদলাবাড়ি ছাড়িয়ে এসে আমরা মালে পৌঁছে বাস-স্টপের পাশে একটা চায়ের দোকানেই খেয়ে নিলাম। দারুণ রসগোল্লা, কালোজাম আর সিঙাড়া। দোকানটাতে খুব ভিড়।
ঋজুদা বলল, ভাল করে খেয়ে নে রুদ্র। জীপ যেরকম মাথা নেড়ে মাঝে মাঝেই আপত্তি জানাচ্ছে, শেষ পর্যন্ত উদোম পথে ঝামেলায় না ফেলে। সারা রাত থাকতে হলে ঠাণ্ডায় কুলপি মেরে যাব।
খেয়ে-দেয়ে আবার এগোলাম আমরা।
চালসাও পেরুনো হল। এখান থেকে ময়নাগুড়ির পথ বেরিয়ে গেছে।
অনেকক্ষণ আগে থেকেই পথের দুপাশে চা বাগান আরম্ভ হয়েছে। বাগানের পর বাগান। কেসিয়া ভ্যারাইটির ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া গাছ, নীচে চায়ের সবুজ নিবিড় সমারোহ পেছনে নগাধিরাজ হিমালয়ের শোভা।
গোঁ গোঁ করে জীপ চলেছে। মাঝে-মধ্যে কোনও চা বাগানের জীপ বা ট্রাকের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। চা বাগানের কুলি-কামিন কাজ সেরে নিজেদের ঘরে ফিরছে গান গাইতে গাইতে। অনেক সাঁওতাল দেখলাম এখানে। কোথা থেকে কোথায় কাজ করতে আসে এরা, ভাবলে অবাক লাগে!
তারপর বানারহাট, বীরপাড়া হয়ে আমরা প্রায় সন্ধের সময় মাদারীহাটে এসে পৌঁছলাম। ডানদিকে কোচবিহারের পথ বেরিয়ে গেছে। সোজা গেলে হাসিমারা হয়ে ফুংসোলিন। ভুটানের সীমান্ত। এপথে একটু এগিয়েই আমরা ডানদিকে চেক-নাকা পেরিয়ে ঢুকে পড়লাম হলঙে।
ঋজুদার কাছ থেকে রিজার্ভেশন স্লিপ দেখে তারপর আমাদের ঢুকতে দিল ফরেস্ট গার্ড। সাদা পাথুরে মাটি আর নুড়ি-ঢালা পথ সোজা চলে গেছে। হলঙের দিকে। সাত কিলোমিটার।
একটু পরই সন্ধে হয়ে যাবে। পথের পাশে পাশে একটি নরম লাজুক ছিপছিপে নদী চলেছে গাছপালা লতাপাতার আড়ালে। পরে জেনেছিলাম যে, এই নদীর নামই হল। নদীর নামে জায়গার নাম। এই সন্ধে হব-হব গভীর জঙ্গলে সেই নদীর মৃদু কুলকুল আওয়াজ ভারী সুন্দর লাগছে। পথের দুপাশে অনেকগুলো ময়ূর দেখলাম। আমাদের জীপের শব্দ শুনে ভারী শরীর নিয়ে কষ্ট করে উড়ে গিয়ে গাছের ডালে বসছিল। রাত প্রায় নেমে এল। এমনিতেই তো ওদের এখন গাছে গিয়ে বসার কথা।
ঋজুদা জঙ্গলে ঢুকলেই কেমন যেন হয়ে যায়। চোখ-মুখ সব পালটে যায়। শহরের ঋজুদা আর জঙ্গলের ঋজুদা অনেক তফাত। স্টীয়ারিংয়ে হাত রেখে পথের দিকে চেয়ে আমাকে ফিসফিস করে ঋজুদা বলল, “চিতা বাঘ বড় শখ করে ময়ূর ধরে খায়, তা জানিস? বড় বাঘও ময়ূর ভালবাসে।
আমি বললাম, ময়ূরের মাংস খেলে নাকি লোকে পাগল হয়ে যায়? ঋজুদা হেসে উঠল। বলল, যে এ কথা বলে, সেও একটি পাগল। ময়ূরের মাংসের মতো মাংস হয় না, তা জানিস? পৃথিবীতে এত ভাল হোয়াইট নেই-ই বলতে গেলে তবে এখন তো ময়ূর ন্যাশনাল বার্ড। ময়ূর মারার প্রশ্নই ওঠে না।
আমি বললাম, চিতাবাঘে মেরে খায় যে!
ঋজুদা বলল, চিতাবাঘের কথা ছাড়। আইন-কানুন, সংবিধান কিছুই মানে না ওরা। ওরা যা খুশি তাই করে।
যখন হলঙ-এর দোতলা কাঠের বাংলোয় গিয়ে পৌঁছলাম আমরা, তখন সবে অন্ধকার নেমেছে। শ্রীবিবেক রায় এলেন আমাদের দেখাশোনা করতে। আমি যখন আড়ালে ডেকে তাঁকে ঋজুদার নাম বললাম, তখন তো তিনি খুব খুশি এবং উত্তেজিত। ঋজুদাকে এসে বললেন, আপনাকে কীভাবে আপ্যায়ন করতে পারি, বলুন?
ঋজুদা হাসল; বলল, কিছু করতে হবে না মশাই, আমার এই চেলাটিকে একটু বাঘ দেখান। পারবেন তো?
বিবেকবাবু বললেন, বাঘ তো এখানে রাস্তার কুকুরের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। তবে দেখা পাওয়া ভাগ্যের কথা। আপনার খাতিরে অবশ্য শুভদৃষ্টি হলেও হতে পারে।
আমি ঋজুদাকে মনে করিয়ে দিলাম, তুমি তেল ভরলে না ঋজুদা, যদি রাতে কোথাও যাও, আর কাল তো ফুংসোলিন যাব আমরা!
ঋজুদা বলল, ঠিক বলেছিস।
তারপর বিবেকবাবুকে বললেন, যাবেন নাকি আমাদের সঙ্গে মাদারীহাট? তেল ভরতে যাব।
বিবেকবাবু বললেন, বরাতে থাকলে ঐটুকু যাওয়া-আসার পথেই বাঘ দেখতে পাবেন। তবে, আমার কাজ সেরে আসি। আরও যাঁরা এসেছেন তাঁদের খবরাখবর সুখ-সুবিধার খোঁজ নিয়ে আসি। ততক্ষণে আপনারা চা খেয়ে চাঙ্গা হয়ে নিন।
ঋজুদা হেসে বলল, ফেয়ার এনাফ।
বিবেকবাবু বললেন, বাঘ যদি সত্যিই সামনে পড়ে, তাহলে জীপ চালাবে কে? ড্রাইভার ভীতু হলে কিন্তু বিপদ।
ঋজুদা বলল, আমিই চালাব, আমিই ড্রাইভার।
এ কথা শুনে বিবেকবাবু একটু চিন্তিত হয়ে পড়লেন। কারণ বাঘ দেখার পর এক-একজন লোকের এক এক রকম অবস্থা হয়। ভগবান বা ভূত দেখার মতো। কিন্তু মুখে কিছুই বললেন না ঋজুদাকে। লজ্জা পেলেন।
আমার মজা লাগল। কারণ ঋজুদাকে আমি যেমন চিনি, উনি তো তেমন চেনেন না।
কোন চা বাগানের প্রেস্টিজ ব্ৰাণ্ড তা জানি না, তবে বিকাশবাবু ফার্স্ট ক্লাস চা দিয়েছিলেন। ডানলোপিলো লাগানো বিছানায় পিঠের নীচে বালিশ দিয়ে বসে ঋজুদা চা খেতে খেতে একটা বড় বোলের পাইপ বের করে ধরাল। পাইপের। মিষ্টি তামাকের গন্ধে ঘর ভরে গেল।
ঋজুদা বলল, কী হে বৎস, আর এক কাপ চা করে খাওয়াও, একটু গুরুসেবা করো, ড্রাইভারের গায়ে জোর করো, নইলে বাঘ দেখে ড্রাইভার অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে তো!
আমি হাসলাম; বললাম, ড্রাইভারকে আমি তো চিনি।
তারপরই আধ চামচ চিনি দিয়ে যথারীতি দুধ কম দিয়ে ঋজুদাকে চা বানিয়ে দিলাম। একটু পরে কাজটাজ সেরে বিবেকবাবু আমাদের মেহগনি কাঠ দিয়ে বানানো ঘরের দরজায় এসে টোকা দিলেন।
কোট-টোট চড়িয়ে, মাথায় টুপি পরে আমরা নীচে নামলাম। ঋজুদা জাপান থেকে একটা জার্কিন কিনে এনেছিল, সেটা পরলে ঋজুদাকে ভীষণ কিম্ভুতকিমাকার দেখায়। ঋজুদা স্টীয়ারিং-এ বসল, মধ্যে আমি; বাঁ-দিকে বিবেকবাবু।
বাংলো থেকে বেরিয়ে হলঙ নদী পেরিয়ে বিবেকবাবুর কোয়াটার্স, মাহুত ও হাতিদের আস্তানা ছাড়িয়ে বড়জোর আধমাইলটাক গেছি আমরা, হঠাৎ বিবেকবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, বাঘ! বাঘ!
দূরে রাস্তার উপরে এক জোড়া লাল চোখ দেখা গেল। ঋজুদা জোরে জীপ ছোটাল। হেডলাইটের আলোয় দেখা গেল একটা বিরাট বড় রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার রাস্তা ছেড়ে বাঁদিকের জঙ্গলে নেমে যাচ্ছেন। আমরা পৌঁছতে পৌঁছতে জঙ্গলে ঢুকে গেলেন তিনি।
বিবেকবাবু উত্তেজিত হয়ে বললেন, দেখলেন?
ঋজুদা বলল, বড় লাজুক বাঘ। তারপর বলল, কী রে রুদ্র, দেখলি?
হুঁ। আমি বললাম।
ঋজুদা বলল, মনে হচ্ছে না দেখলেই খুশি হতিস।
আমি বিবেকবাবুর সামনে লজ্জা পেয়ে বললাম, যাঃ!
পাঁচ মিনিটও হয়নি, আবার বিবেকবাবু বললেন, বাঘ! বাঘ!
ঋজুদা জোরে অ্যাসিলারেটরে চাপ দিল। দেখতে দেখতে বাঘের মুখোমুখি! মাঝারি সাইজের রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। রাস্তার ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখছে।
ঋজুদা স্টার্ট বন্ধ করে দিয়ে হেডলাইটটা জ্বালিয়ে রাখল বাঘের উপর। দশ হাত দূর থেকে বাঘটা অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল আমাদের দিকে। সন্দেহের চোখে। তারপর আস্তে আস্তে রাস্তা ছেড়ে বাঁদিকের খোলামতো জায়গায় নেমে গিয়ে একটা বড় সেগুন গাছের নীচে বসে পড়ল আমাদের দিকে মুখ করে।
ঋজুদা ফিসফিস করে বলল, বিবেকবাবু, মনে হচ্ছে আপনাকে পছন্দ হয়েছে।
বিবেকবাবুর বাঁ পাটা বাইরে ছিল। টক করে পাটা ভিতরে টেনে নিলেন উনি।
ঋজুদার কথায় ও বিবেকবাবুর পা সরানোর শব্দে বাঘের কান খাড়া হয়ে উঠল।
আমি বললাম, ঋজুদা, ব্যাক করে চলল। অ্যাটাক করবে।
ঋজুদা বলল, বলছিস তুই? বলেই, একটু ব্যাক করল জীপটা স্টার্ট দিয়ে।
দেখলাম, জীপের পেছোনোর সঙ্গে সঙ্গে বাঘটাও মুখ ঘুরিয়ে যাচ্ছে। আমাদের দিকে আস্তে আস্তে।
আবার স্টার্ট বন্ধ করে দিল ঋজুদা। জার্কিনের পকেট থেকে দেশলাই বের করে ফস্ করে পাইপ ধরাল।
বাঘটার কানটা আবার খাড়া হয়ে উঠল।
ঋজুদা বলল, ভাল করে দেখ নে রুদ্র, নইলে কলকাতায় গিয়ে বন্ধুদের গুল মারলে ওরা তোর সম্বন্ধে সন্দেহ করবে।
দুসস, আমি বললাম। বললাম বটে, কিন্তু আমার বুকের কাছটা ব্যথাব্যথা করছিল। ভীষণ গরম লাগছিল। গলা শুকিয়ে শুকনো হয়ে গেছিল। একটু জল হলে ভাল হত।
কোথাও কোনও শব্দ নেই। শুধু জঙ্গলের গন্ধ। ডানদিকের হল নদীর কুলকুল শব্দের সঙ্গে ভেজা মাটির সোঁদা সোঁদা গন্ধ। আর বাঘের গায়ের বোঁটকা গন্ধ। ঋজুদার পাইপে নিকোটিন আর জল জমে যাওয়ায় প্রত্যেক টানের সঙ্গে হুঁকোর মতো ভুড়ক ভুড়ক আওয়াজ বেরোচ্ছে।
এমন সময় বিবেকবাবু ফিসফিস করে বললেন, এমন খোলা জীপে বাঘের এত কাছে বসে থাকা কি ঠিক হবে?
ঋজুদা বলল, কথা বলবেন না মশায়!
বাঘটা একদৃষ্টে আমাদের দিকে তাকিয়ে নট-নড়নচড়ন নট-কিছু হয়ে বসে আছে তো আছেই। সেও আমাদের দেখছে, আমরাও তাকে দেখছি। শুভদৃষ্টি হল শেষ পর্যন্ত।
অনেকক্ষণ পরে ঋজুদা জীপ স্টার্ট করল। জীপ স্টার্ট করতেই বাঘটা উঠে দাঁড়াল। জীপটাকে ফাস্ট গীয়ারে দিয়ে একটু সামনে গড়িয়ে দিতেই বাঘটা উঠে দাঁড়িয়ে জীপের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। সমস্ত শরীরটা চার পায়ের মধ্যে ঝুলিয়ে দিয়ে।
হঠাৎ ঋজুদা খুব জোরে অ্যাকসিলারেটরে চাপ দিল। ইঞ্জিনের শব্দে ও হঠাৎ এগিয়ে যাওয়াতে বাঘটা একটু হকচকিয়ে গেল।
একটু দূরে গিয়ে ঋজুদা জীপটাকে থামাল।
আমরা পেছন ফিরে দেখলাম, বাঘটা রাস্তার মাঝখানে এসে আমাদের জীপের দিকে তাকিয়ে আছে। জীপটা থেমে যেতেই এক পা এক পা করে জীপের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল।
আমার হঠাৎ মনে হল, কলকাতাটা কী সুন্দর জায়গা! এমন সন্ধেবেলায় বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলনের আলোজ্বলা মেলায় ঘুরে বেড়াতে পারতাম মজা করে, তা নয়, ঋজুদার সঙ্গে এসে কী বিপদেই পড়লাম!
হঠাৎ হো-হো করে হেসে উঠল ঋজুদা। তারপর জীপটা স্টার্ট করে এগিয়ে চলল।
বাঘটাকে তখনও লক্ষ করছিলাম আমি ঘাড় ঘুরিয়ে। কিছুদূর হেঁটে এসে ও নাক তুলে আমাদের চলমান জীপের দিকে চেয়ে রইল।
বিবেকবাবু বললেন, হাসছেন কেন?
মজা দেখে, ঋজুদা বলল।
আমি বিরক্ত গলায় বললাম, মজাটা কীসের?
ঋজুদা গীয়ার বদলে বলল, বাঘটা বাচ্চা। এসব হচ্ছে বাচ্চা বাঘের স্বভাব। ও যা করছিল, তা সবই ওর অদম্য কৌতূহলের ফল। ওর কাছ থেকে কোনওই ভয় ছিল না। কিন্তু বিপদ ছিল ওর মায়ের কাছ থেকে। অবশ্য যদি জীপ থেকে নামতিস। ওর মা ধারেকাছেই ছিল।
আমি অবাক হয়ে বললাম, অত বড় ধেড়ে বাঘ যদি বাচ্চা হয়, তাহলে তো আমিও বাচ্চা!
ঋজুদা বলল, তুই তো বাচ্চাই। তুই যে নিজেকে বড় বলে সব সময় জাহির করতে চাস, এইটেই প্রমাণ করে যে তুই বাচ্চা।
স্বল্প-পরিচিত বিবেকবাবুর সামনে ঋজুদার এমন কথাবার্তা আমার পছন্দ হল না। চুপ করে রইলাম।…
.
অন্ধকার থাকতে থাকতে দরজায় ধাক্কা দিয়ে, টি-কোনিতে মোড়া টি-পটে করে গরম চা দিয়ে গেল বেয়ারা। হলঙের সমস্ত টুরিস্ট লজটা জেগে উঠেছে। বাথরুমে বাথরুমে জল পড়ার শব্দ হচ্ছে। ইলেকট্রিক আলো নেই। জেনারেটরের আলো সন্ধে থেকে রাত দশটা অবধি জ্বলে।
যখন আমরা কাঠের সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামলাম, দেখি চারটে হাতি দাঁড়িয়ে আছে পিঠে গদি নিয়ে। বনবিভাগের হাতি। ঋজুদা আর আমি একটা হাতির পিঠে উঠে পড়লাম। অন্য হাতিগুলোতে অন্য ঘরের লোকেরা। তারপর হাতিগুলো চলতে লাগল একসারিতে।
তখনও ম্লান চাঁদ আছে। শীতের শেষরাতে কুয়াশা, শিশির আর চাঁদে কেমন মাখামাখি হয়ে গেছে। সারা আকাশের বনেজঙ্গলে কোনও জাপানী চিত্রকর যেন ওয়াশের কাজের কোনও ছবি এঁকেছেন।
রাস্তার দু পাশে কতগুলো উঁচু উঁচু সোজা মেরুদণ্ডের গাছ। গাছগুলোর গায়ের রঙ সাদা। গুঁড়িগুলো মজার। খোপ খোপ করা। ঋজুদাকে শুধোলাম, কী গাছ এগুলো?
ঋজুদা বলল, তোকে ধরে মারব আমি। বাঙালীর ছেলে শিমুল গাছ চিনিস না?
একটু পরই অন্ধকার হালকা হতে লাগল। হেঁয়ালির রাত শেষ হয়ে প্রাঞ্জল দিন ফুটতে লাগল ফুলের মতো। হাতিরা হলঙ নদী পেরুল। জল থেকে ঠাণ্ডার ধোঁয়া উঠছে। ময়ূর ডাকল এদিক ওদিক থেকে। দেখতে দেখতে রুপো গলে গিয়ে সোনা এল। বুলবুলি জাগল, ময়না জাগল, টিয়ার ঝাঁক কোথায় না কোথায় কথা রাখতে তীরের মতো উড়ে গেল ট্যাঁ-ট্যাঁ করতে করতে।
আমরা শিমুল অ্যাভিন ধরে চলতে লাগলাম।
মাহুত বলল, এ পথটা গেছে জলদাপাড়ায়। যেখানে আমাদের বনবিভাগের পুরনো বাংলো আছে।
দুধারে গভীর বন। শাল, সেগুন, রাই-সেগুন। বড় বড় পুড়ী ঘাস– পাতা তাদের চওড়া, সতেজ, সবুজ। শিশু গাছ সরু সরু। ডানদিকে পড়ে আছে বিস্তীর্ণ তৃণভূমি খেয়ালী তোসা নদীর ফেলে-যাওয়া পথে। গভীর জঙ্গলের ফাঁক-ফোঁক দিয়ে চোখে পড়ে। গণ্ডারের আস্তানা ওখানে।
এই হল-জলদাপাড়ার জঙ্গল ঘিরে আছে অনেক নদনদী। ভারী সুন্দর এদের নাম সব। হল, বুড়ি তোসা, তোসা, চূড়াখাওয়া, বেলাকোওয়া আর মালঙ্গী।
একটু দূর গিয়ে পথ ছেড়ে বাঁদিকের নুনীতে নামল হাতিগুলো। এখানে জঙ্গল ফাঁকা করে কিছুটা জায়গায় মাটির সঙ্গে নুন মিশিয়ে রাখে বনবিভাগের লোকো। জংলী জানোয়ারেরা নুনের নেশায় আসে এখানে। জানোয়ারেরা তো আর বিড়ি-সিগারেট, পান-টান খায় না–ওদের নেশা বলতে নুন খাওয়া। হরিণ সম্বর অবশ্য মহুয়ার দিনে মহুয়া খেয়ে নেশা করে ভাল্লুকরাও। এই নুনী থেকে পায়ের দাগ দেখে সেই পায়ের দাগ অনুসরণ করে হাতি নিয়ে জঙ্গলে ঢোকে মাহুতরা।
আমি ঋজুদাকে বললাম, কী থ্রিলিং! এসে ভালই করেছি, কী বলো?
ঋজুদা ইয়ার্কি করল আমার সঙ্গে, বলল, যা বলেন!
তারপর বলল, বুঝলি রুদ্র, ঘণ্টা কয়েকের জন্যে বেশ রাজারাজড়া কি মন্ত্রী-টন্ত্রী মনে হচ্ছে না নিজেদের? যতদূর দেখা যায়, গাছগাছড়া, মানুষ কাঁকড়া সবকিছুর মালিক আমরা। হুজুর মা বাপ। বলো, হাতির পিঠে কেমন যাচ্ছি?
আমি বললাম, তা ঠিক। কিন্তু কোমরে ব্যথা করছে।
ঋজুদা চাপা হাসি হাসল। বলল, ভাত আর আলু খাওয়া বন্ধ কর, আইসক্রীমও। এতটুকু ছেলে, পেটে চর্বি থাকবে কেন?
হঠাৎ মাহুতরা মুখ দিয়ে একটা অদ্ভুত আওয়াজ করে হাতিগুলোকে এক এক করে নুনী থেকে বের করে আনল। পথে উঠতেই দেখলাম, দুটো গাঢ় খয়েরী রঙের বেশ বড় হরিণ ছুটে রাস্তা পেরিয়ে এদিকে জঙ্গল থেকে ওদিকের জঙ্গলে গেল।
হরিণ! হরিণ! করে চারটে হাতি থেকে জনা পনেরো লোক সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল। আর সেখানে হরিণ থাকে? মাইল দুয়েক চলে যাবে বোধহয় এক দৌড়ে।
ঋজুদা গম্ভীর মুখে বলল, বনবিভাগকে সাজেস্ট করব যে, সকলের মুখ ভোরবেলা স্টিকিং-প্লাস্টার দিয়ে সেঁটে দেবে।
আমি ফিসফিস করে বললাম, কী হরিণ ওগুলো? ওড়িশাতে তো দেখিনি? বিহারেও না!
ঋজুদা বলল, এগুলো হডিয়ার। এগুলো এই রকম জঙ্গলেই দেখা যায়। আমাদের কাজিরাঙ্গায় গেলে দেখতে পাবি সোয়াম্প ডিয়ার। আরও বড় হয়। জলকাদা ঘাসবনে পাওয়া যায় ওগুলো।
এবারে মাহুতেরা হঠাৎ খুব সাবধানী হয়ে গেল। হাতিগুলোর সঙ্গে কী সব সাংকেতিক ভাষায় কথাবার্তা বলতে লাগল। মাঝে মাঝে ডাঙ্গসের বাড়ি মারতে লাগল মাথায়। একটা হাতির সঙ্গে একটা ছোট সুনটুনী-মুনটুনী বাচ্চা ছিল। সেটা মায়ের পায়ে পায়ে যাচ্ছিল, মাঝে মাঝে মা দাঁড়িয়ে পড়লেই চুকচুক করে একটু দুধ খেয়ে নিচ্ছিল। ঋজুদা ফটাফট তার ছবি তুলছিল।
হাতিগুলো ডানদিকের নলবনে খুব সাবধানে এগোতে লাগল। এত গভীর নলবন যে হাতি ডুবে যায়। নলের ফুলগুলো কী সুন্দর! যার চোখ আছে সে-ই দেখতে পায়। রুপোলি আর লালে মেশা কী নরম রেশমী ফুলগুলো। গালে চেপে ধরে চুমু খেতে ইচ্ছে করে।
ঋজুদা ফিসফিস করে কী শুধোল যেন মাহুতকে।
মাহুত বলল, তেঁড়া। বলেই সতেজ সবুজ ঘাসের বনে ঢুকল।
সবুজ পাইপটা জার্কিনের পকেটে ঢুকিয়ে রেখে, ক্যামেরাটা দুহাত দিয়ে ধরল ঋজুদা।
আমরা একটা জায়গায় এসে পড়লাম, সেখানে ঘাসের বন বিরাট জায়গা জুড়ে জমির সঙ্গে সমান হয়ে গেছে। গণ্ডার বা গেঁড়ারা রাতে এখানে শুয়েছিল। ভারী চমৎকার সবুজ, নরম নিত্য-নতুন বিছানা ওদের। মাথায় গাছের চাঁদোয়া– নীচে ঘাসের বিছানা, পাতার বালিশ। দিব্যি আছে।
এ জায়গায় পৌঁছে হাতি ও মাহুতেরা একটু আড়ষ্ট হয়ে গেল। হঠাৎ বড় হাতির মাহুত কী একটা আদেশ করল তার হাতিকে। হাতিগুলো একে একে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ঘাস জঙ্গল ভেঙে এগোতে লাগল। এদিকে বড় বড় পুড়ী ঘাস, চওড়া সতেজ সবুজ পাতা এদের। সোজা উঠেছে।
এখন গাছের চাঁদোয়া নেই। নীল আকাশে রোদ চকচক করছে। মাথার উপরে বাজপাখি উড়ছে চক্রাকারে। দারুণ এক সুগন্ধী প্রভাতী নিস্তব্ধতা চারিদিকে। শুধু হাতির পা ফেলার নরম শব্দ ছাড়া কোনও শব্দ নেই।
সামনে চোখ পড়তেই আমি স্তব্ধ হয়ে গেলাম। সেঞ্চুরিয়ান ট্যাঙ্কের মতো তিনটে একশিঙা গণ্ডার ও একটা বাচ্চা গণ্ডার দাঁড়িয়ে আছে সামনের ফাঁকা জায়গাটাতে। তাদের পেছনে আদিগন্ত নলবন। খেয়ালী তোসর ফেলে-যাওয়া পথে গজিয়ে-ওঠা নল। আরও দূরে মেঘ-মেঘ ভুটান পাহাড়। ওদের দুপাশে সবুজ সুস্পষ্ট পুড়ীর জঙ্গল। পায়ের নীচে মিষ্টি গন্ধের বাংলার মাটি, নুড়ি, সাদা বালি। মাথার উপরে ঝকঝকে নীল আকাশ। ওদের নাকে স্বাধীনতার গন্ধ, চোখে সাহসের দ্যুতি।
কতক্ষণ যে তাকিয়েছিলাম মনে নেই তা। হঠাৎ এক ভদ্রমহিলার হাত থেকে একটা চা-ভর্তি থামোফ্লাস্ক থপ করে নীচে পড়ল।
ব্যাস্। গণ্ডারগুলোর মধ্যে চঞ্চলতা দেখা গেল। ওরা পরাধীন হাতির পিঠে-বসা শিক্ষিত, জামা-কাপড় পরা ভীতু প্রাণীগুলোর থেকে দূরে, আরও দূরে সরে যেতে লাগল।
দিগন্ত ওদের সবসময় হাতছানি দেয়। খোলা আকাশ, খোলা বাতাস ওদের ডাকে। ওরা আমাদের পেছনে ফেলে ঘৃণায় পা ফেলে ফেলে, অবহেলায়, দ্রুত চলে যেতে লাগল।
ওদের যতক্ষণ দেখা গেল, চুপ করে চেয়ে রইলাম। চোখের দূরবীক্ষণেও যখন ওদের আর দেখা গেল না, ওরা মিলিয়ে গেল দিগন্তের নলবনে, তখন হুঁশ হল আমার।
ঋজুদা বলল, তাহলে এবার ইডেনে গো-হারান ডাংগুলি খেলা না দেখে ভালই করেছিস বল?
আমি হেসে ফেললাম।
বললাম, যা বলেছ। টিকিট না পাওয়ার জন্যে আর দুঃখ নেই।
ঋজুদা বলল, কলকাতা ফিরে তোর সব বন্ধুদের বলবি, ক্রিকেট ছাড়াও উত্তেজনাকর আরও অনেক কিছু আছে। আমাদের বনবিভাগ এত সুন্দর সব বন্দোবস্ত করে রেখেছে, তোরা ছেলেমানুষরা যদি এসব না দেখবি, প্রকৃতির মধ্যে এসে প্রকৃতিকে না উপলব্ধি করবি, না জানবি, তাহলে এত আয়োজন কাদের জন্যে?
আমি অনেকক্ষণ চুপ করে থাকলাম। ভাল লাগায় আমার বুক ভরে উঠেছিল।
হাতিগুলো এবারে দূরের নলবনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকল।
এরাও কি দিগন্তের দিকে যাচ্ছে? এই জড়বুদ্ধি পরাধীন জানোয়ারগুলোরও কি স্বাধীন হওয়ার শুভ ইচ্ছা জাগল মনে? এদের নাকেও কি খোলা আকাশ, খোলা বাতাসের বাস লেগেছে?
কে জানে!