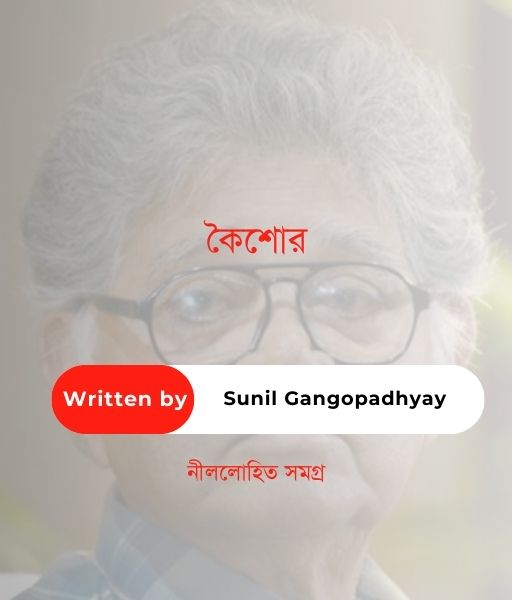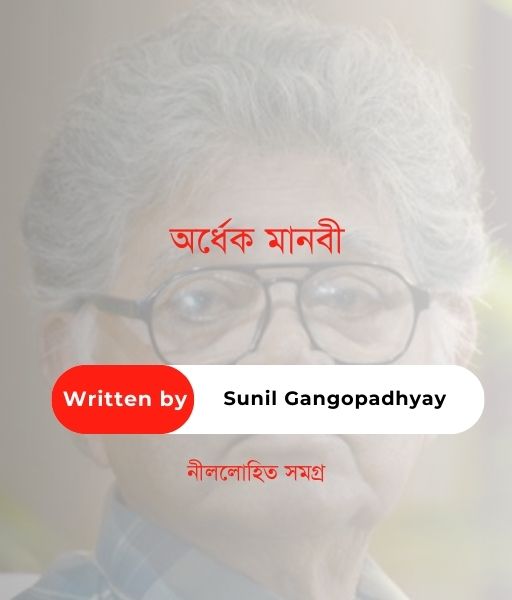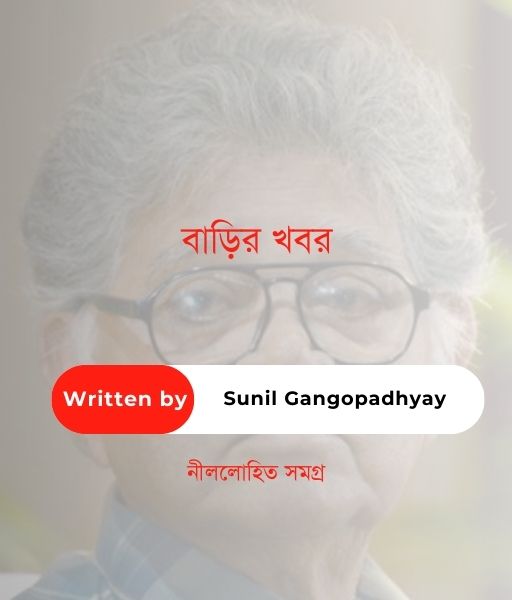নীললোহিতের চোখের সামনে
‘নাগরদোলা ঘুরছে, আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, ‘জোরে, আরও জোরে ঘোরাও! আরও! দুধ-সাবু খেয়ে চালাচ্ছ নাকি? আরও জোরে?’
বিপরীত দিকের দোলনটা থেকে সেই মেয়েটি ভয় পেয়ে বলল, ‘এই, এই, আর না, আর না—আমার মাথা ঘুরছে! থামাও থামাও!
সুন্দরী মেয়েকে ভয় দেখাতে কার না ইচ্ছে হয়! হোক-না অচেনা! আমি লঘু গলায় ফের দোলনাওয়ালাদের উত্তেজিত করতে লাগলাম, ‘না, না থামবে না! আরও জোরে!’
মেয়েটি এবার আমার দিকে তাকিয়ে বলল, ‘না, না, খুব খারাপ হবে বলে দিচ্ছি! দোলনা ছিঁড়ে পড়বে!’
আমি বললাম, ‘অত ভয় পেলে নাগরদোলায় উঠতে গেছেন কেন?’ এই থেকে আলাপ। শান্তিনিকেতনের পৌষ মেলায় ঘুরন্ত বাতাসের মধ্যে দেখা। এক দোলনায় আমরা চারজন, অন্য দোলনায় ওরা। আমাদের দোলনায় বন্ধু, তার স্ত্রী ও শ্যালকের সঙ্গে আমি, ও-দোলনায় ওরা চারজন মেয়ে। সেই মেয়েটির গায়ের রং কুচকুচে কালো। কিন্তু অমন রূপসী মেয়ে কদাচিৎ চোখে পড়ে। সবার চোখ ঘুরে-ঘুরে ঐ মেয়েটির দিকেই আসবে। কালো ঝকঝকে শরীর তার পরনে সাদা শাড়ি, ব্লাউজ সাদা, চটি সাদা, হাতে ঘড়ির ব্যান্ডটাও সাদা, আর—কোন অলংকার নেই—গলায় শুধু একটা শ্বেত মুক্তামালা। কোনারকের সুরসুন্দরী মূর্তি যে দেখেছে সেই শুধু মেয়েটির রূপ খানিকটা অনুমান করতে পারবে!
নাগরদোলা থামল, ওরা নেমে পড়তেই আমি বললাম, ‘একি, হয়ে গেল? আর-একবার ঘুরবেন না?’
অচেনা মেয়েরা সবসময় অনুরোধ বোঝে না। অনুরোধকে মনে করে ‘আওয়াজ দেওয়া’। সেই মেয়েটি কিছু বলবার আগেই তার সঙ্গিনী অন্য একটি বার্লি-খাওয়া চেহারার মেয়ে বলল, ‘কী অসভ্য ছেলেগুলো, চল কৃষ্ণা—’
নাম জানলাম, কৃষ্ণা। আমার এক পিসিরও গায়ের রং ছিল খুব কালো —নাম ছিল পূর্ণিমা। অচেনা লোকজনের মধ্যে তাঁকে পূর্ণিমা বলে ডাকলে তিনি হেসে আকুল’ হতেন। বলতেন, ‘চেঁচিয়ে ডাকিস্ না–লোকে পূর্ণিমা শুনে তাকিয়ে দেখবে কালো একখানা অমাবস্যা!’
হোমিওপ্যাথিক ওষুধের রোগ নির্ণয়ের মতন শান্তিনিকেতন মেলায় সবাই সবার কোনো-না-কোনো সূত্রে চেনা। বিকেলবেলা আমার বন্ধুর সঙ্গে বেড়াতে গেলাম তার এক অধ্যাপক বন্ধুর বাড়িতে। সেই অধ্যাপকের আবার এক অন্যবন্ধুর ছোটবোনের চারজন বান্ধবী বেড়াতে এসেছে। ওরকম সম্পর্ক ধরলে পৃথিবীর সবাই যে সবাইকার বন্ধু-বান্ধবী, মানুষ সেটা ভুলে যায়। সুতরাং আমার বন্ধুর বন্ধুর ছোট বোনের চারজন বান্ধবীকে আমি মোটেই পর ভাবলাম না। আপন—আপন ভেবে বিনাদ্বিধায় আলাপ-পরিচয় শুরু করে দিলাম। নাগরদোলার সেই চারজন, তাদের মধ্যে কৃষ্ণা।
অনেক মেয়ের কালো রঙের জন্য লজ্জা থাকে। কৃষ্ণার নেই, কৃষ্ণা অহংকারী। সে জানে, সব পুরুষই তার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে বাধ্য। চায়ের কাপ ঠোঁট থেকে নামিয়ে কৃষ্ণা বলল, ‘আপনি ভারি পাজি। নাগরদোলা অত জোরে চালাতে বলছিলেন কেন?’
আমি বললাম, ‘চলুন, আমার সঙ্গে আবার চড়বেন আসুন! আমি ভয় ভাঙিয়ে দিচ্ছি!’
কৃষ্ণার সঙ্গিনী সেই বার্লি-খাওয়া মেয়েটি কড়া চোখে তাকাল। তাকে দেখলেই মনে হয়—ভবিষ্যতে সে কোন মেয়ে হস্টেলের সুপারিনটেন্ডেন্ট হবে। তা হোক, তাতে আমার কোন ভয় নেই। আমারই পেড়াপিড়ি ও আগ্রহাতিশয্যে ফের দলবল মিলে সবাই এলাম নাগরদোলায় চাপতে। এখন তো আলাপ হয়ে গেছে, এখন আর দ্বিধা কী! নাগরদোলায় প্রবল ঘূর্ণির মধ্যে আমি কৃষ্ণার বাহু চেপে ভয় দেখিয়ে বললাম, ‘এবার ফেলে দিই? দিই ফেলে?’ বাচ্চা বালিকার মতন কৃষ্ণা হাসতে-হাসতে ভয় পেতে লাগল। আমি এমনিতে একটু বোকা—সোকা, লাজুক ধরনের ছেলে, কিন্তু কৃষ্ণার পাশে বসে হঠাৎ যে কী করে সেদিন অত চালু হয়ে গেলাম, কে জানে!
কলকাতা শহরটা আসলে খুব ছোট। কৃষ্ণার সঙ্গে কথা বলতে-বলতে বেরিয়ে পড়ল—যদিও কৃষ্ণা থাকে বালিগঞ্জে—আমি থাকি চরম উত্তর কলকাতায় —তবু ওর চেনা কয়েকজনকে আমি চিনি—আমার চেনা কয়েকজনকে চেনে কৃষ্ণা। ঐ যে আগেই বলেছি, বন্ধুর বন্ধুতেই পৃথিবীটা ভর্তি।
শান্তিনিকেতনে আমি একদিন বেশি থেকে গেলাম, আগের দিন চলে গেল কৃষ্ণারা। যাবার আগে কৃষ্ণা ওর বাড়ির ঠিকানা ও টেলিফোন নাম্বার লিখে দিয়ে গেল, আমিও দিলাম আমারটা। স্টেশনে দাঁড়িয়ে ট্রেন ছাড়ার আগে বেশ আন্তরিকভাবেই বলল, ‘বাড়িতে আসবেন কিন্তু একদিন। ঠিক আসবেন!
শান্তিনিকেতন থেকে চলে গেলাম মাসাঞ্জোর, সেখান থেকে দুর্গাপুর ঘুরে কলকাতায় ফিরলাম সাতদিন বাদে। রাত্তিরবেলা জি টি রোড ধরে বন্ধুর জিপে করে আসছিলাম, সেদিন চাঁদের আলো পৃথিবীটা ধুইয়ে দিচ্ছে। হঠাৎ মনে পড়ল কৃষ্ণার কথা।
কিন্তু কৃষ্ণাকে আমি কোনদিন ফোন করিনি, চিঠি লিখিনি, দেখা করতেও যাইনি। কেন? ঠিক কারণটা আমি নিজেও জানিনা। এইজন্যই তো আমি গল্প লিখতে পারিনা। গল্পে যা-যা মানায় তার কিছুই ঠিকমতো আমার মাথায় আসেনা। শান্তিনিকেতনে অমন চমৎকারভাবে যে-রূপসী মেয়েটির সঙ্গে আলাপ হল, নিজের হাতে ঠিকানা লিখে দিয়ে যে কলকাতায় আবার দেখা করতে বলল—তার সঙ্গে দেখা করে পরিচয় আরও ঘনিষ্ঠ করাই তো স্বাভাবিক, গল্পেও সেইরকম হয়। কৃষ্ণার সেই ঠিকানা লেখা কাগজটা এখনো আমার কাছে আছে—অথচ একদিনও আর দেখা হয়নি।
আমি কেন দেখা করিনি? একজন মানুষের মধ্যে অন্তত পঞ্চাশজন মানুষ লুকিয়ে থাকে। একই মানুষ, কিন্তু মায়ের সামনে, অফিসের বড়বাবুর সামনে, বন্ধুর সামনে, স্ত্রীর সামনে এবং প্রেমিকার সামনে, ছোটভাইয়ের সামনে-সে বিভিন্ন, বলা যায় সম্পূর্ণ আলাদা ব্যক্তিত্ব। সেইরকম, যে-মানুষ শান্তিনিকেতনে পৌষমেলায় বেড়াচ্ছে আর যে কলকাতার ভিড়ের বাসে ঝুলছে—এরা দুজনেও আলাদা। শান্তিনিকেতনে কৃষ্ণার সঙ্গে কথা বলার সময়ে কোন দ্বিধা ছিল না, বিনা ভূমিকায় অনায়াসেই লঘু চাপল্য এবং ইয়ারকি শুরু করতে পেরেছি। কিন্তু কলকাতায় অন্যরকম। শান্তিনিকেতনের সেই একখানা বিরাট আকাশ, লাল ধুলোর রাস্তা, মেলার হট্টগোল আর সোনাঝুরি গাছে হাওয়ার ঢেউ—এই পটভূমিকার বদলে ট্রামলাইন পেরিয়ে গলিতে ঢুকে বাড়ির নম্বর খুঁজে—দরজার কলিংবেল বাজিয়ে বা কড়া নেড়ে বৈঠকখানায় বসে কৃষ্ণার সঙ্গে দেখা হলে সবকিছু অন্যরকম হতে বাধ্য। টেলিফোন করেই-বা কী বলব? বলব কোথাও দেখা করতে? নিয়ে যাব কোন রেস্টুরেন্টে? যাকে নাগরদোলায় চাপার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম, তাকে কি ঠিক সেই একইভাবে রেস্টুরেন্টে আসার আমন্ত্রণ জানানো যায়? আমি ভেবে পাইনি। আমি আর দেখা করিনি কৃষ্ণার সঙ্গে।
দেখা করিনি, কিন্তু ক্ষীণ আশা করেছিলাম—কৃষ্ণা নিজে হয়তো আমাকে চিঠি লিখবে বা দেখা করবে। আবার জানতাম, তা অসম্ভব। কোন মেয়ে যেচে কোন ছেলেকে চিঠি লেখে নাকি আগে?—ছেলেটিকে তার ঠিকানা দেওয়া সত্ত্বেও! আর, কৃষ্ণা ওরকম ঝলমলে রূপসী—তার নিশ্চয়ই অনেক অনুরাগী—তার বয়েই গেছে আমার মতন হেঁজিপেঁজিকে চিঠি লিখতে।
পৌষমেলা হয় শীতকালে তখন প্যান্ট-কোট পরার সময়। কৃষ্ণার ঠিকানা লেখা কাগজটা রয়ে গেল আমার কোটের পকেটে। শীত ফুরোলে কোটটা কাচতে না-দিয়েই আলমারিতে তুলে রাখলাম। পরের বছর শীত যখন পড়ি-পড়ি করছে—গরম জামাগুলো সব নামতে শুরু করেছে—কোটের পকেট থেকে অন্য অনেক কাগজপত্রের সঙ্গে বেরুল সেই ঠিকানা লেখা টুকরো কাগজটা। মনে পড়ল আবার কৃষ্ণার কথা, সেই কষ্টিপাথরের মতন উজ্জ্বল মসৃণ দেহ, সেই শিশুর মতন সরল পবিত্র মুখ, মনে পড়ল সেই শ্বেতবসনা সুন্দরীকে। বুকের মধ্যে একটু টনটন করে উঠল। কৃষ্ণা খুব আন্তরিকভাবে বলেছিল ওর সঙ্গে কলকাতায় দেখা করতে। কেন দেখা করিনি! এখন কী করব! ধুৎ, কী পাগলামি! একবছর আগে দেখা হয়েছিল এখন গিয়ে বলা যায়, আমি এসেছি, এতদিনে আমার সময় হল!
কাগজটা কোটের পকেটেই রয়ে গেল। প্রত্যেক বছর প্রথম শীতে কোটের পকেট থেকে সবকিছু বার করি—অনেক পুরোনো কাগজপত্র বাতিল হয়ে যায়, ছিঁড়ে ফেলি, কিন্তু সেই ঠিকানা লেখা কাগজটা ফেলতে ইচ্ছে করেনা। চোখ বুলিয়ে আবার রেখে দিয়ে ভাবি, থাক্-না। পড়ে-পড়ে কৃষ্ণার ঠিকানা ও ফোন নাম্বার আমার মুখস্থ হয়ে গেছে—তবু ওর নিজের হাতের লেখাটা ফেলি না! এই একটা অদ্ভুত ব্যাপার—এই একটা বাড়ির ঠিকানা আমার মুখস্থ-যে বাড়িতে আমি কখনো যাইনি সাত বছর কেটে গেছে, আর কখনো যাবও না। কৃষ্ণার টেলিফোন নাম্বার আমার মনে গাঁথা হয়ে গেছে। অথচ ঐ নাম্বার কোনদিন আমি ডায়াল করিনি। কত দরকারি ঠিকানা, কত গুরুত্বপূর্ণ টেলিফোন নাম্বার ভুলে গিয়ে কত অসুবিধা হয়—কিন্তু সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় কৃষ্ণার ঠিকানা ও টেলিফোন নাম্বার আমার
স্মৃতিতে চিরস্থায়ী। এরকম অযৌক্তিক কাণ্ড করলে কি আর গল্প হয়?
বরং মাঝে-মাঝে ভাবি কৃষ্ণা তো একবার ভাবলেও পারত—ওর ঠিকানা—লেখা কাগজটা আমি হারিয়ে ফেলেছি—ওর ঠিকানা বা টেলিফোন নাম্বারটা আমার মনে নেই—সুতরাং ইচ্ছা থাকলেও আমি ওর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারিনি। কিন্তু ওকি আমায় একটা চিঠিও লিখতে পারত না? কিংবা টেলিফোন? এই ভেবে কৃষ্ণার ওপর প্রবল অভিমান হয় আমার।