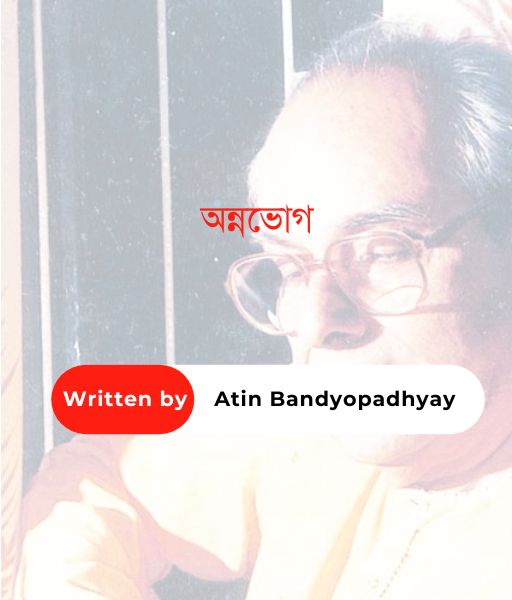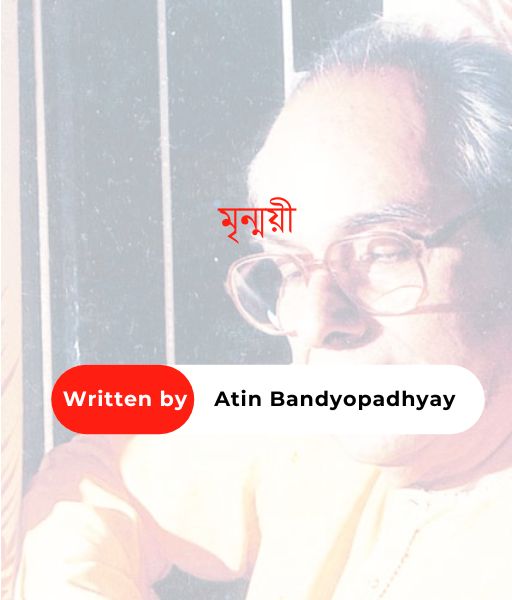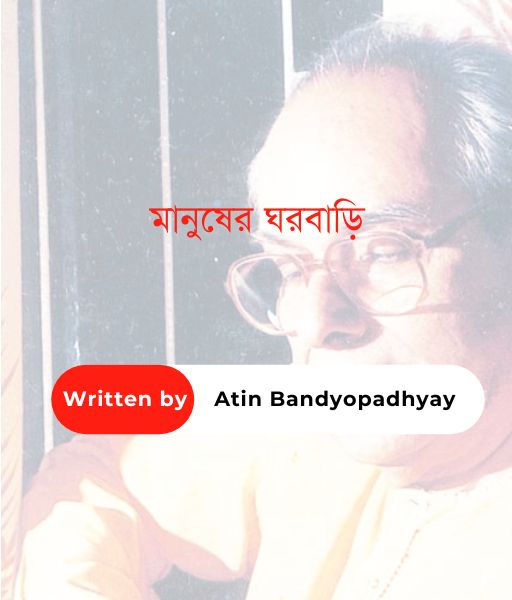নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে (Neelkantho Pakhir Khoje) – দ্বিতীয় খণ্ড : 20
এভাবে বাংলাদেশে কিছু সময় কেটে গেল। এভাবে বাংলাদেশে ২১শে ফেব্রুয়ারি চলে এল একদিন।
সারারাত জেগেছিল বলে সফিকুর এখন হাই তুলছে। বড় খাটুনি গেছে। সারারাত সে এবং তার কলেজের বন্ধুরা মিলে শহরময় পোস্টার মেরেছে। ঘরে মেয়েরা পোস্টার লিখে দিচ্ছে আর ওরা দেয়ালে দেয়ালে সেঁটে দিয়ে এসেছে। কলেজের মেয়েদের উপর ছিল পোস্টার লেখার ভার। ওদের কাজ সেগুলি সকাল না হতে মেরে দিয়ে আসা। সকাল হলেই শহরের মানুষেরা দেখবে কারা যেন রাতারাতি এই শহরকে ২১শে ফেব্রুআরির জন্য নানা রঙের ফেস্টুনে সাজিয়ে দিয়ে গেছে। উৎসবের মতো এই শহর—প্রায় ঈদ মুবারক।
সফিকুর এইমাত্র ঘরে ফিরেছে। ফিরেই হাতমুখ ধুয়েছে। অন্য দিনের মতো সে সাইকেলটা বারান্দায় তুলে রাখেনি। কারণ সে আবার সাইকেলে দেখতে বের হবে রাতে, রাতে ওরা কতদূর পর্যন্ত পোস্টার মেরে আসতে পেরেছে। সুতরাং সাইকেলটা বাইরে রেখে নিত্যদিনের মতো একটু টেবিলে গিয়ে বসা।
সকালে সে দুটো একটা কবিতা আবৃত্তি করতে ভালোবাসে। অথবা আজ যেন সারাটা দিন শুধু কবিতা আবৃত্তি আর গান। মাঠের ভাষা, বাংলা ভাষা। মানুষের ভাষা, বাংলা ভাষা। এমন দিনে সে কবিতা পড়বে না তো কবে পড়বে। রবীন্দ্রনাথ অথবা নজরুল থেকে সে কবিতা পড়তে ভালোবাসে। ফতিমা এলে সে জীবনানন্দ আওড়ায়। ফতিমা কাছে থাকলে তার অন্য কবিতা আর ভালো লাগে না-সে তখন ফতিমার কালো চোখের দিকে তাকিয়ে হাসে, তারপর ধীরে ধীরে কেমন এক অসীমে ডুবে যাবার মতো সে ফতিমার কাছে ঘন হয়, যেন চুলের ঘ্রাণ নিতে নিতে তার মুগ্ধ স্বভাবের ভিতরে ডুবে যাবে এবার, বলবে, কখন মরণ আসে কে বা জানে—কালীদহে কখন যে ঝড় ফসলের নাল ভাঙে—ছিঁড়ে ফেলে গাংচিল শালিখের প্রাণ জানি নাকো,–তবু যেন মরি এই মাঠঘাটের ভিতর…। এই দেশ, বাংলাদেশ, এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি–ফতিমার ছোট ছোট কালো বেথুন ফলের মতো চোখ দেখতে দেখতে সফিকুরের এমন মনে হলে বলে, আমি যাব তোমার দেশে। সোনালী বালির চরে সূর্য ওঠা দেখব। তরমুজের জমিতে ঈশমনানার ছই দেখব। আর দেখব সেই অর্জুন গাছ। গাছে গাছে এখন কত না ডালপালা। তুমি আমি তার নিচে দাঁড়িয়ে আমাদের বাংলাদেশ দেখব। ফতিমা এসব শুনলে কেমন চুপ হয়ে যায়। চোখমুখ বড় ভারি, গম্ভীর এবং কথা বলতে চায় না। তখন সফিকুর অকারণ হাসে। ফতিমাকে রাগিয়ে দিতে না পারলে সে মজা পায় না। ফতিমা কথা না বললে সে জানে একটু খোঁচা দিলেই সে কথা বলবে। রাগাবার জন্য তখন সে বলবে, ওডা আবার একটা দ্যাশ নাহি! সফিকুর ফতিমার মতো বাঙাল টান রাখবে গলায়। তখন ফতিমা আরও ক্ষেপে যায়। রাগে অভিমানে মুখ ভার করে থাকে। চায়ের কাপ হাতে থাকলে সেটা ফেলে ভিতরে চলে যায়। মাঝে মাঝে সফিকুর ওর কথা নিয়ে বড় বেশি ব্যঙ্গ করে। সে আর রাগ চাপতে পারে না। আর রাগের কথা বললে ওর মুখে তখন আরও বেশি বাঙাল কথা বের হয়ে আসে। সফিকুরের সঙ্গে ফতিমা কিছুতেই বাঙাল কথা বলতে চায় না। যতটা সে পারে ধীরে ধীরে বইয়ের ভাষায় কথা বলার চেষ্টা করে। কঠিন কাঠ কাঠ গলা না করে খুব সুন্দর এক জলতরঙ্গ আওয়াজের মতো গলা করার চেষ্টা করে। এবং তখনই যত দুষ্টুবুদ্ধি সফিকুরের। ওর ইচ্ছা কেবল ফতিমা ওর সঙ্গে বাঙাল কথা বলুক। এমন সুন্দর করে সে যে কী করে কথা বলে; প্রাণের ভিতর কেমন মায়া জাগানো ওর গলার স্বর। ফতিমাকে বাঙাল কথার ভিতর যতটা চেনা যায়, ওর মতো কথা বললে তেমন চেনা যায় না।
আঞ্জুর সঙ্গে সাধারণত সফিকুর ফতিমাদের বাড়ি যায়। ফতিমাকে যে সফিক ভাই অকারণ রাগিয়ে দিতে ভালোবাসে বার বার বলেও সে তা ফতিমাকে বোঝাতে পারে না। তখন তার সোজাসুজি বাংলা কথা—আর কইয়েন না। ঠিক নিয়া যামু একবার আমাগ নদীর চরে। দ্যাখবেন দ্যাশ কারে কয় একখানা আপনেগ দ্যাশ আবার দ্যাশ নাহি? দুধ-মাছ পাওয়া যায় না। মানুষগুলাইন গঙ্গার পানি খাইয়া থাকে। ইলিশ মাছ মিলে না গণ্ডায় গণ্ডায়। আছে কিডা তবে?
—কেন আমাদের রবীন্দ্রনাথ আছে। বিদ্যাসাগর নজরুল আছে।
—ছাড়ান দ্যান। আমাগ নাই কিছু বুঝি মনে করেন? চিত্তরঞ্জন দাশ, হকসাহেব, জীবনানন্দ অগ বাড়ি কলকাতায় আছিল, না!
—আমি বলেছি ওদের বাড়ি কলকাতায় ছিল?
—তবে মুর্শিদাবাদে।
সফিকুর মুর্শিদাবাদের ছেলে। কথায় কথায় ফতিমা রেগে গেলে বলবে, মীরজাফরের দেশের মানুষ ভালো হবে কী করে? বিশ্বাসঘাতক। এ দেশের নুন খাবে এ দেশটাকে বলবে—এডা আবার দ্যাশ নাহি। কোনটা দেশ। এমন পলাশফুল শীতে কোথাও ফোটে? এমন শিমুলের বন আপনি নদীর পাড়ে পাড়ে আর কোথাও দেখেছেন? কী বলুন। চুপ করে কেন? তারপর চুপচাপ যেন বলার ইচ্ছা, বাংলাদেশের মানুষ আমার সোনাবাবুকে পৃথিবীর আর কোথাও গেলে পাবেন? কিন্তু কিছু বলতে পারে না। সোনাবাবুর কথা মনে হলেই গলার স্বর ভারি হয়ে আসে।
কত অকারণ এই ঝগড়া। অথচ এমন না হলে ভালো লাগে না সফিকুরের। এমন না হলে ফতিমাকে সে ঠিক চিনতে পারে না। অভিমানে তখন ফতিমা আর তার বাড়ি আসে না। সেও যায় না। কিন্তু কতদিন। ফতিমা নিজেই পারে না। আঞ্জুর সঙ্গে চলে আসে। যেন সে সফিকুরের কাছে আসেনি। সফিকুরের সঙ্গে কোনও দরকার নেই। যত দরকার তার মায়ের সঙ্গে। যত গল্প তার মায়ের সঙ্গে। যাবার সময় দেখাও করে যেত না বোধ হয়। কেবল আঞ্জু টেনে নিয়ে আসে বলে দেখা না করে পারে না। সফিকুর তখন এই অকপট মেয়ের কাছে ধরা দিতে ভালোবাসে। সে আর তাকে অবহেলা করে না।
রাস্তা পার হলেই ফতিমাদের সুন্দর কাঠের রেলিং দেওয়া বাড়ি। নানারকম ফুলের গাছ মাঠে! একটা দেবদারু গাছ আছে। তার নিচে ছোট্ট কাঠের চেয়ার। ঘাস মসৃণ। সামসুদ্দিনসাহেব শীতের দিনে সেখানে বসে রোদ পোহান। ফতিমা যখন বাবাকে চা দিয়ে আসে সফিকুর তার দোতলা ঘর থেকে দেখতে পায়। সুন্দর একটা নীল রঙের শাড়ি পরতে ফতিমা ভালোবাসে। যখন সদর পার হয়ে টুক করে ওদের বাড়িতে ঢুকে যায়, কী অকারণ তখন ফতিমার ভয়। সবাই দেখে ফেলল এই ভয়। সে বার বার আঁচলে মুখ মুছতে থাকে। কেন যে মুখে ঘাম, সফিকের কাছে যেতে গেলেই ঘাম আঁচলে বার বার মুছেও মুখের প্রসাধন সে ঠিক রাখতে পারে না। ফতিমা সফিকের কাছে এলে সেজন্য প্রসাধন করে আসে না। কারণ, সে জানে সফিকের কাছে এসে সে তার প্রসাধন ঠিক রাখতে পারবে না। ফতিমা আসলে কপাল না মুছে পারে না। ভিতর ভিতর এভাবে সফিকের জন্য কী একটা মায়া গড়ে উঠেছে। সফিকও সেটা বুঝতে পারে। কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলতে সাহস পায় না। সামসুদ্দিনসাহেব ওর জন্য খুব করেছেন। এই শহরে সে রিফুজি। সামসদ্দিনসাহেবের আপ্রাণ চেষ্টা না থাকলে সে তার সংসার চালিয়ে পড়াশোনা চালাতে পারতো না। আর এই এক মেয়ে যে তাকে আরও সব নতুন উদ্যমের কথা শোনাচ্ছে। সে মাঝে মাঝে একা একা শীতের রাতে টের পায় কোথাও এই মেয়ের প্রাণে বড় একটা ক্ষত আছে। ফতিমা কেন যে মাঝে মাঝে বড় বিষণ্ণ হয়ে যায়। তখনই দেয়ালের বিচিত্র পোস্টার, সেই পোস্টারে বুঝি নতুন সংগ্রামের কথা লেখা হচ্ছে। সফিক ফতিমার সঙ্গে সেই সংগ্রামের শরিক হতে চায়। ওরা রাত জেগে তখন পোস্টার লেখে।
সফিকুর বই সামনে রেখে কিছুক্ষণ বসে থাকল। ওর মা কখন চা রেখে গেছে সে টের পায়নি। সে জানালায় শীতের সূর্য উঠতে দেখছে। সূর্যের আলোতে শত শত পোস্টার দেয়ালে সকাল হবার সঙ্গে সঙ্গে ফুটে উঠেছে। বার বার সেইসব পোস্টারের লেখাগুলি ওর চোখের উপর ভেসে যাচ্ছে। পোস্টারে ফতিমা, আঞ্জু আরও সব মেয়েরা সারারাত লিখে গেছে, বড় বড় অক্ষরে লিখে গেছে—মোদের গরব মোদের আশা আ মরি বাংলাভাষা। কোনও পোস্টারে ফতিমা ওর সুন্দর হস্তাক্ষরে লিখেছে— একুশে ফেব্রুআরি পালন করুন। আঞ্জু লিখেছে—নাজিম-নুরুল চুক্তি রোখো, নইলে সুখের গদি ছাড়!
দেয়ালে দেয়ালে এমন সব বিচিত্র পোস্টার। সে জানালা খুলে, সারারাত যেসব পোস্টার মেরে এসেছে, যা সে দাঁড়িয়ে দেখার সময় পায়নি, এখন এই সকালে তার কিছু কিছু দেখে তার বুক কেমন ভরে উঠেছে। তার হেঁটে যেতে ইচ্ছা হচ্ছে। যেন হেঁটে গেলে অজস্র পোস্টারের ভিতর কোনটা ফতিমার হাতের লেখা সে চিনতে পারবে। এমন নিবিষ্ট হয়ে কে আর রাতের পর রাত পোস্টার লিখে গেছে! সে তার পোস্টারে বার বার বাংলাদেশ কথাটা নিচে লিখে দিতে চেয়েছে। কখনও বোঝা যায় রাগে অথবা বড় অভিমানে সে একটা গাধার লম্বা মুখ এঁকে দিয়ে নাজিম নুরুলের ছবি আঁকতে চেয়েছে। এতটুকু ক্লান্তি ছিল না। কে যে তাকে এমনভাবে প্রেরণা দিচ্ছে সফিক বুঝতে পারছে না। একটানা ফতিমা উপুড় হয়ে কাজ করে গেছে। আজ ভোর রাতে শুধু সে একবার গিয়ে দেখেছে যারা লিখছে তাদের ভিতর ফতিমা নেই। ফতিমাদের নিচের বারান্দায় কাঠের রেলিঙের ধারে মোমের আলোতে সবাই লিখে চলেছে। শেষ রাতের দিকে শহরের আলো নিভে গিয়েছিল—ওরা অন্ধকারে চুপচাপ বসে থাকেনি, মোমের বাতি জ্বালিয়ে নিয়েছে। তুলির এক-এক টানে ওরা এক-একটা পোস্টার শেষ করেছে।
সফিকুর ফতিমাকে না দেখে কেমন অবাক হয়ে গেছিল। সে নেই, এটা সে ভাবতে পারছে না। সে গিয়ে শুয়ে আছে, আর সবাই লিখছে এটা ভালো দেখাচ্ছে না। সে ভিতরে ভিতরে রুষ্ট হয়ে উঠেছে। পোস্টারগুলি একসঙ্গে করে বড় প্যাকেট করল একটা। কেরিয়ারে বেঁধে নেবার সময় ভাবল আঞ্জু অথবা রমাকে বলবে, ফতিমা কোথায়? কিন্তু যে মেয়ে ওকে না বলে ভিতরে শুতে চলে যায় তার সম্পর্কে খোঁজখবর করতে ইচ্ছা হয় না। কী ভীষণ ঠাণ্ডা। হাত-পা শীতে সাদা হয়ে গেছে। ফতিমার এ সময় এটা ঠিক হয়নি। মনে মনে সে ফতিমার হয়ে কার কাছে যেন ক্ষমা চাইছে। আর তখনই সে দেখল দোতলার রেলিঙে চুপচাপ একা ফতিমা। অস্পষ্ট আলোতেও সফিকুর চিনতে পারে সব। মাথার উপর শীতের আকাশ। বুড়িগঙ্গা থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া উঠে আসছে। কিছু পালের নাও হয়তো এখন উজানে বৈঠা মারছে। সে এ-ভাবে একা দাঁড়িয়ে আছে কেন, শীতের রাতে, ঠাণ্ডা হাওয়ার ভিতর দাঁড়িয়ে আছে কেন—এই সব জিজ্ঞাসা করতে সাইকেল ফেলে উপরে উঠে গেল। ডাকল, এই ফতিমা।
ফতিমা পিছন ফিরে তাকাল না। বুঝি সে শীতের আকাশ দেখছে। রাত ফর্সা হতে দেরি নেই। হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী এবার প্রভাতফেরিতে বের হবে। ফতিমা বুঝি ওদের মুখে বাংলাদেশের গান শুনতে পাচ্ছে। সকাল হলেই একুশে ফেব্রুআরির ডাকে মা-বোনেরা জেগে উঠবে।
সফিক ফের বলল, ফতিমা, তুমি এখানে দাঁড়িয়ে আছ! শরীর খারাপ লাগছে? তারপর সফিক কী বলবে ভেবে পেল না। তা’ছাড়া এখানে এ সময়ে দুজনে একসঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক না। কেউ দেখে ফেললে সামসুদ্দিন সাহেবের কানে উঠতে পারে। যতবারই সে ফতিমার সঙ্গে থাকে প্রায় দল বেঁধে থাকে। একবার সে আর ফতিমা মধুর ক্যান্টিনে একা বসে থাকলে, ফতিমা ভীষণ অস্বস্তিতে বিরক্ত বোধ করেছিল। বলেছিল, সফিক ভাই, আমি বাড়ি যাব।
সফিকুর বুঝতে পেরেছিল সেদিন, ফতিমা চায় না ওরা দু’জনে এভাবে একা পলিয়ে পালিয়ে দেখা করে। নিজের মানুষ চুরি করে দেখতে যাওয়া বড় অপমানের। সে সেই থেকে কখনও ফতিমাকে আর কোথাও একা দাঁড়িয়ে থাকতে বলেনি। এখানেও সে আসত না। তবু কেন যে এমন শীতের রাতে ওকে এভাবে একা দেখে সফিকুর বিচলিত হয়ে পড়েছিল। সে চুপি চুপি উঠে এসেছে। ফতিমা ওর কথার কোনও জবাব দিচ্ছে না। ফতিমা হয়তো এভাবে আসা তার পছন্দ করছে না। সফিকুরের ভিতরটা দুঃখে কেমন ভার হয়ে গেল। বলল, আর তোমার সঙ্গে দেখা হচ্ছে না। আমি শেষবারের মতো এগুলি সেঁটে বাড়ি চলে যাব। তোমরা সাবধানে থেকো।
ফতিমার কেমন চমক ভাঙল। সে ঘাড় ফেরাল, দেখল সে আর সফিক বড় কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছে। ওর গায়ে সেই বাদামী রঙের পাঞ্জাবী, খোপকাটা লুঙ্গি আর পায়ে এক জোড়া স্লিপার। চোখমুখ দেখলেই মনে হচ্ছে হাত-পা শীতে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে সফিক কাশছে। এ সময় ওকে একটু চা করে দিলে বড় ভালো হতো। ওকে কাশতে দেখেই যেন বলল, প্যাকেটগুলি রেখে দিন। অন্য কাউকে দিয়ে ওগুলি দেয়ালে সেঁটে দেব। আপনি বরং বসুন। চা করে আনছি। দেরি হবে না।
—আরে না না। এখন আর ঝামেলা বাড়িয়ো না। রাত ফর্সা হতে না হতে হাতের কাজ সব সেরে ফেলতে হবে। আমি যাচ্ছি। বলেই সে দু’পা গিয়ে আবার ফিরে এল। বলল, কেউ তোমাকে কিছু বলেছে? এখানে একা দাঁড়িয়ে আছ!
ফতিমা হাসল।—না না। কে কী বলবে?
—কী জানি কত রকমের কথা উঠতে পারে। এ ক’দিন যেভাবে বেহুঁশ হয়ে আমরা পোস্টার লেখা, সাঁটা এবং দল বেঁধে কাছাকাছি থেকেছি, কথা উঠতে কতক্ষণ।
—আজ এমন বলতে নেই। তুমি সাবধানে থেকো। এই প্রথম সে সফিককে তুমি বলে লজ্জায় মাথা নিচু করে রাখল। তারপর খুব আস্তে আস্তে বলল, আমার জন্য তুমি ভেবো না।
সফিকের মনে হল সারা উপত্যকায় ফুল ফুটে আছে। সে ফতিমাকে নিয়ে উপত্যকায় কেবল ছুটছে। শীতের রাতে যে সামান্য উষ্ণতা তার দরকার ছিল ফতিমার এমন কথায় সে তা ভুলে গেল। বলল, যদি খোঁজ করতে চাও মেডিক্যাল হোস্টেলে যেও। আমাকে সেখানে পাবে। আমরা সেখান থেকেই ১৪৪ ধারা ভাঙব ভাবছি।
ফতিমা বলল, তোমার সঙ্গে সারাদিন ঘুরে বেড়াতে পারলে কী যে ভালো লাগত সফিক। এমন দিন তো আর আমাদের আসবে না।
সফিকের মনে হল শীতে যেন কাঁপছে ফতিমা। সে বলল, এখানে দাঁড়িয়ে আর ঠাণ্ডা লাগাবে না। ভিতরে যাও।
ফতিমা অনুগত ছাত্রীর মতো নেমে গেলে ফের ডাকল, আচ্ছা, তুমি এখানে এই ঠাণ্ডায় চুপচাপ কেন দাঁড়িয়েছিলে? এভাবে একা দাঁড়িয়ে থাকলে আমার কেন জানি ভয় হয়।
বলল, এমনি। মনের ভিতর কী যে কখন থাকে কেউ তা বলতে পারে না। সারারাত ফতিমা আর একজন মানুষের চোখমুখ ভেবেছে এবং গভীরে ডুবে গেলে শরীরে তার চন্দনের গন্ধ টের পায়। সে যেন তার পাশেই দাঁড়িয়ে বলছে, ফতিমা তুই কী ভাল ভাল কথা লিখে যাচ্ছিস রে! আমি কী লিখব? আমাকে তোর পাশে বসে লিখতে দিবি?
—কেন দেব না?
—কী জানি, যদি না দিস। যদি বলে দিস, তুমি স্বার্থপর। তুমি বাংলাদেশের মানে জান না। তোমার কোন অধিকার নেই লেখার।
—যা, এমন বলব কেন! আমি তো বাপু তোমার মুখের দিকে তাকিয়েই লিখে যাচ্ছি। আমি যে এত করছি কার জন্য? তোমার জন্য!
—আচ্ছা, তোর ঐ সফিক কে হয় রে?
—সফিক বড় ভালো ছেলে। আমি তাকে ভালোবাসি। আমার বাবাও সেটা টের পেয়েছে। আমি ওকে না পেলে এখন বুঝতে পারছি বাঁচব না।
—তা হলে আমি তোর কে?
—তুমি যে আমার কে, বুঝতে পারি না। তুমি আমার কী যে নও মাঝে মাঝে আবার তাই ভাবি যখন আমি মরে যাব, কবরের নিচে চলে যাব বুঝি তখন দেখব তুমি আমার কবরের পাশে বসে আছ। তুমি আছ আমার পাশে পাশে। তুমি বাদে আমি এ-বাংলাদেশে সব থাকলেও একা।
—যা! তুই সব বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যা বলছিস!
—তুমি চলে যাবার পর আমার এটাই মনে হয়েছে। তুমি এমন বলবে জানতাম। তবে তুমি যেখানে যে ভাবেই থাক, তুমি আমার। আমার মাটির, আমার কাছের মানুষ
তখনই ওর পাশে এসে সফিকুর দাঁড়িয়েছিল। ফতিমা টের পায়নি সফিকুর পাশে দাঁড়িয়ে আছে। পরে টের পেলে সে যেন ধরা পড়ে গেছে এমনভাবে তাকিয়েছিল। সে সফিককে বলল, আমি আমার মনের মানুষকে ভাবছি সফিক। সে আমাকে ফেলে দূরে চলে গেছে। আর এদেশে আসবে কিনা জানি না। আর দেখা হবে কিনা জানি না। এমন দিনে তাকে না ভেবে থাকতে পারিনি। তুমি বিশ্বাস কর সফিক, আমার মনে হয়েছে শুধু আমি আর তুমি সারারাত জেগে পোস্টার লিখিনি, সেও আমাদের সঙ্গে লিখে গেছে। তাকে ভালো করে দেখার জন্য কতদিন পর এখানে একাকী এসে দাঁড়িয়েছিলাম। তুমি এ-সব না-ই জানলে!
ফতিমা সফিকুরকে উত্তরে কিছু না বলে অন্য কথায় চলে গিয়েছিল, তুমি আর ঠাণ্ডা না লাগিয়ে সকাল সকাল একটু ঘুমিয়ে নাও। কিন্তু সফিকুরকে তখন ভারি বিমর্ষ দেখাল, ফতিমা আবার না বলে পারল না; ভয়ের কী আছে সফিক? সে তো আমাদেরই মানুষ
সফিক বলল, কে সে?
ধরা পড়ে গেল বুঝি! তবু সে কিছুক্ষণ স্থির তাকিয়েছিল সফিকের দিকে। তারপর বলেছিল, সোনাবাবুর কথা বলছি।
—অ, তোমার সেই সোনাবাবু যে আমার মতো নিজের দেশ ছেড়ে পালিয়েছে। কিন্তু ফতিমা সোনাবাবু সম্পর্কে আর কোনও কথা বলল না। সে বলল, আর দেরি করো না। রাত ভোর হয়ে আসছে।
সফিক বলল, সাবধানে থেকো।
সফিক কেন যে বার বার একই কথা বলছে! ফতিমা বলল, ভয়ের কী আছে সফিক! আজকের দিনে আমরা তো আর একা নই! সারা বাংলাদেশ যখন আছে সোনাবাবু যখন আছে তখন আর ভয় কী! সে তো আমাদের সব সময় আরও সাহসী হতে বলছে। তোমাদের সঙ্গে আমরাও মার্চ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে যাব। আজকের দিনে অন্তত তুমি আমাকে ঘরে থাকতে বলো না।
সফিক বলল, আমি বারণ করব না। এমন দিনে বারণ করতে নেই জানি। যা কিছু কাজ সব সেরে ফেলতে হবে। এই শীতের ভোরে এর চেয়ে বেশি কিছু ভাবতে পারি না।
টেবিলের সামনে বসে তার ভোর রাতের সব কথা মনে হচ্ছিল। জানালা বন্ধ ছিল বলে ঘর অন্ধকার। সে জানালা খুলে দিলে সব কিছু পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে। শীতের রোদ লম্বা হয়ে নামছে মাটিতে। সে বইয়ের পাতা পর পর উল্টে গেল। যেখানে চোখ আটকে গেল—কী সুন্দর সেই সব পঙ্ক্তি। যেন ওর সামনে ফতিমা দু’হাত তুলে ভালোবাসা মেগে নিচ্ছে। সে চোখ বুজে ওর সেই কথাগুলি যেন বলে গেল—স্থির জেনেছিলাম, পেয়েছি তোমাকে, মনেও হয় নি–তোমার দানের মূল্য যাচাই করার কথা। তুমিও মূল্য কর নি দাবি
রোদটা তখন আরও লম্বা হয়ে ঘরে ঢুকে যাচ্ছে। শীতের রাস্তায় কারা তখন মার্চ করে চলে যাচ্ছে। ওদের বেয়নেটে নরম রোদ তীক্ষ্ণ ফলার মতো কেঁপে কেঁপে যাচ্ছে। সফিকুর যেন সেইসব শূন্য দেয়ালে বার বার আঘাত হানার জন্য পড়ছিল, জোরে জোরে সে পড়ছে—তোমার কালো চুলের বন্যায়—আমার দুই পা ঢেকে দিয়ে বলেছিলে–তোমাকে যা দিই, তোমার রাজকর তার চেয়ে বেশি—আরো দেওয়া হল না—আরো যে আমার নেই!
শহরের বড় রাস্তায় মার্চ-পাস্টের দৃশ্য। রাইফেলের বাঁটে রোদ পিছলে যাচ্ছে। কলের পুতুলের মতো দম দেওয়া মনে হচ্ছে ওদের। দম ফুরিয়ে গেলেই যেন সব জারিজুরি ওদের শেষ হয়ে যাবে। সফিকুর এবার জানালাটা বন্ধ করে দিল। কুচকাওয়াজের দাপটে, এমন যে প্রেরণার কথা শোনাতে চেয়েছিল, তারা তা শুনতে পেল না। এবার সে রাস্তায় তাদের হাঁক দিয়ে বলে যাবে, বলে গেলেই শীতের মাঠে আবার পাখিরা এসে বসতে পারবে। কলের পুতুলের ভয়ে ওরা আজ মাঠ ছেড়ে কোথাও যাবে না। সফিকুর তাড়াতাড়ি নাকে মুখে দুটো গুঁজে রাস্তায় বের হয়ে গেল।
সেই শীতের সকালে সোনাকে দেখা গেল কলকাতার বড় রাস্তা ধরে হাঁটছে। চোখে-মুখে ভীতির ছাপ এই বড় শহর দেখে গাড়িঘোড়া দেখে সে কেমন আড়ষ্ট হয়ে হাঁটছে। যারা বাবুমানুষ, তাদের সে জিজ্ঞাসা পর্যন্ত করতে ভয় পাচ্ছে, কোথায় সেই নির্দিষ্ট বাসটি পাওয়া যাবে। ওরা ওর ওপর রাগ করতে পারে। সে ভয়ে ভয়ে ঠেলাওলা অথবা যাদের দেখলে তার ভয় লাগে না, যারা তার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনবে তেমন মানুষকে খুঁজছিল। সে দু’জন ভদ্রলোককে কিছু বলতে গিয়ে দেখেছে—ওরা এত ব্যস্ত যে তার কথা শুনতেই পাচ্ছে না। হাত তুলে কোনও রকমে ওর সঙ্গে দয়া করে দায়সারাভাবে কথা বলে ছুটে যেন পালাচ্ছে। ওর মনে হল ওরা পালাচ্ছে, ওরা ওর কথা কেউ শুনতে চাইছে না। তবু কেন জানি একজন বুড়োমতো মানুষ তাকে খুব যত্নের সঙ্গে বুঝিয়ে দিল, ঐ যে মনুমেন্ট দেখছ, তার নিচে তুমি বাস পাবে।
কলকাতায় তেমন শীত পড়ে না। তবু ওর ভিতরে শীত ভাবটা বড় বেশি জাঁকিয়ে বসেছে। হাল্কামতো কুয়াশা চারপাশে। সামনের রাস্তাটা যে চৌরঙ্গি, ডান দিকে যে বাড়ি সিংহের ছবি সদর দরজায় এবং ওটা যে লাটভবন, সোনা তাও জানে না। বড় মাঠ দেখলেই গড়ের মাঠ মনে হয়, সে কেবল বুঝতে পেরেছিল, সামনের মাঠটাই গড়ের মাঠ। এবং মাটি, গাছপালা আর মনোরম শীতের সকালে কোথাও র্যামপার্ট থাকতে পারে, কোথাও এই মাঠে র্যামপার্ট আছে ভাবতেই সে একটু সাহস পেল। সকালের রোদ তেমন জোরালো নয়। শীতের হাওয়া কার্জন পার্কের গাছপালায়। সে একটা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে শীতে কাঁপছে। সে শুনে এসেছিল—কলকাতায় তেমন শীত পড়ে না। সুতরাং ওর শীতের জামা না থাকলেও কলকাতায় সে শীতে কষ্ট পাবে না ভেবেছিল। একটা পাতাল পাজামা, কিড্স ব্যাগ কাঁধে, পায়ে কতদিনের পুরানো কেড্স জুতো। কলকাতায় শীত নেই সে শুনে এসেছিল, কিন্তু এসে তক দেখছে সারাক্ষণই শীত। সে শীতে কাঁপতে কাঁপতে বাস ধরার জন্য হাঁটছে।
বাসের ভিতর উঠেও সে খুব নড়ছিল না। চুপচাপ বসে আছে। বেশি নড়াচড়া করলে ওকে কনডাকটার নামিয়ে দিতে পারে। কোথাকার গ্রাম থেকে ভূত এসে কলকাতা নগরীতে হাজির। কী করে যে সোনা এমন ভীতু মানুষ হয়ে গেল! চার বছরে সে আগের সোনা নেই, অন্য সোনা হয়ে গেছে। সেই যে সে ভেবেছিল, এই দেশে এসেই ওরা সবাই রাজার মতো হয়ে যাবে, কত সমরোহ থাকবে জীবনে, দেশ ভাগের নিমিত্ত ওরা শহিদ হয়ে গেছে—সুতরাং সর্বত্র ওদের জন্য বিজয় পতাকা উড়বে। ওরা রাজার মতো হেঁটে হেঁটে শহর নগর পার হয়ে যাবে। সহসা সোনা এবার নিজেকে বাসের ভিতর চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করল, কেমন আছো রাজা? ভালো আছো? শীত করছে খুব? খুব খিদে পেয়েছে? কাল রাত থেকে কিছু খাওনি? আর বেশি দেরি নেই। যেখানে যাচ্ছি, দেখবে কত কিছু খেতে পাবে তুমি। কোন কষ্ট থাকবে না তোমার।
হালিশহরের ক্যাম্পজীবন, রাইট লেফট আর মার্চপাস্ট করে কল্যাণী ক্যাম্পে যাওয়া এসবের ভিতর কতকালের একটা জীবন নির্ভয়ে কেটে গেছে! সে নিজেও জানত না আজ তাকে এখানে আসতে হবে! সে জানত না, এই শহর ছেড়ে, বাংলাদেশ ছেড়ে তাকে কোথাও চলে যেতে হবে। চিঠিতে কী লিখেছে মজুমদারসাহেব তার জানার কথা নয়। তবু এই চিঠিই তার সব। মজুমদারসাহেব তার হয়ে এই চিঠি দিয়েছেন। ভদ্রা জাহাজের সেকেণ্ড অফিসারকে লেখা। সে চিঠিটা দেখালেই তাকে নিয়ে নেবে। তার ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলান্টিয়ার ফোর্সের ট্রেনিং নেওয়া আছে। ট্রেনিং থাকলে নিতে বিশেষ অসুবিধা হয় না। ওর হয়ে মজুমদারসাহেব আর কী লিখেছেন সে জানে না।
বাসের ভিতর শীতের সকাল, তার পাশে গঙ্গানদী। সে বসে বসেই নদী এবং নদীতে জাহাজ দেখতে পেল। এবং বাসটা মোড় ঘুরতেই সব আবার অদৃশ্য হয়ে গেল। ফোর্ট উইলিয়মের দুর্গ দেখতে পেল। এখানে এক র্যামপার্টের পাশে বড় জ্যাঠামশাই এসে বসতেন। এই নদীর পাড়ে এবং কোনও গাছের ছায়ায় তার পাগল জ্যাঠামশায়ের মুখ ভেসে উঠলে সে কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেল।
মেজ জ্যাঠামশাইর বড় প্রিয় এই গঙ্গা নদী। নদীর পাড়ে তিনি তাঁর দেহ রাখবেন এখন কেবল এই আশা তাঁর। আর কিছু তিনি চান না। শীতের সকালে হেঁটে হেঁটে এক ক্রোশের মতো পথ চলে যান গঙ্গাস্নান করতে। নদীর নামেই তাঁর যত পুণ্য। সংসারের প্রতি এখন মনে হয় মায়া মমতা তাঁর কম। এখানে এসে যে এই বয়সে কী করবেন ভেবে না পেয়ে কেবল বাড়িটার চারপাশে নানারকমের গাছ এনে লাগাচ্ছেন। বাবা দু’মাস পর পর ফেরেন। এখানে আসার পর পর সে আর বাবাকে হাসতে দেখেনি। মা রাতে কাঁথার ভিতর শুয়ে কষ্ট পান। শিয়রে একটা কুপি জ্বলতে থাকলে সোনা টের পায় মার চোখমুখ কতটা বিবর্ণ হয়ে গেছে। এখানে এসে তার পর পর আরও দুটো ভাই হয়েছে। জমি-জায়গা বলতে চারপাশের বন জঙ্গল সাফ করে বসতি করা। জঙ্গল সাফ করতে করতে বড়দার হাঁটু শক্ত হয়ে গেছে। ছোটকাকা আর এখানে থাকেন না। নিজের মতো করে তিনি আলাদা শহরে বাস তুলে নিয়ে গেছেন। কাকিমা এসেই এ ববস্থা করে নিয়েছে। বড় জ্যেঠিমা যেদিন সবাই উপবাস থাকে, অর্থাৎ যেদিন সংসারে কিছু জোটে না, পেঁপে সিদ্ধ অথবা শুধু মিষ্ট কুমড়ো সেদ্ধ খেয়ে থাকতে হয় সেদিন রাতে ভাঙা বাক্স থেকে যত চিঠি আছে বের করে পড়েন। রাত জেগে কুপি জ্বালিয়ে জ্যেঠিমা সারারাত বুঝি চিঠি পড়েন। জ্যাঠামশাইর চিঠি। বিয়ের পর পরই যেবার তিনি কলকাতায় শেষবাবের মতো কাজ করতে গিয়ে ছ’মাস ছিলেন, তখনকার কিছু চিঠি। জ্যেঠিমা সকালেই স্নান করে একটা ভাঙা আয়নার সামনে হাঁটু গেড়ে বসেন। কপালে সিঁদুর পরেন বড় বড় ফোঁটায়। এবং তখন জ্যেঠিমাকে দেখলে মনে হয় না সংসারে গতকাল সবার হা-অন্ন গেছে। জ্যেঠিমার এই মুখ দেখলে সোনা চোখের জল রাখতে পারে না। মা না খেয়ে শীতের কাঁথায় শুয়ে থাকলে তার পড়াশুনা করতে ভালো লাগে না। ওরা সবাই আশায় আশায় বসে থাকে বাবা ফিরে আসবেন। যা কিছু অর্থ ছিল বছর তিনের ভিতর শেষ। এখন আছে তিনটে কুঁড়েঘর আর কিছু অন্নহীন প্রাণ। কেউ আর টাকা নিয়ে আসে না। প্রতাপ চন্দের ছেলে লিখেছে তারা দেশ ছেড়ে চলে আসছে। তার কাছে কিছু প্রাপ্য টাকা ছিল। সব খোয়া গেলে সোনা বুঝতে পারে না বাবা এবারে কী করবেন। বাবার চোখমুখের দিকে তাকানো যায় না। ক্রমে বাবা কেমন হয়ে যাচ্ছেন। তবু বাবাই একমাত্র মানুষ যিনি বাড়ি ফিরে এলে ওরা ক’দিন দু’বেলা পেট ভরে খেতে পায়। আবার চলে গেলে সারা সংসারে অন্ধকার। অন্নহীন এই সংসারে সোনার নিজেকে বাড়তি লোক বলে মনে হয়। তখন মনে হয় সকাল হলেই সে ঘুম থেকে উঠে দেখবে, পাগল জ্যাঠামশাই এসে গেছেন এদেশে। তিনি আর পাগল নন। তিনি বড় মানুষ, তাঁর অর্থবল অনেক। কোথাও তিনি এক রাজবাড়ি কিনে রেখেছেন। সবাইকে নিয়ে তিনি এখন সেখানে যাবেন। সবাইকে তৈরি হয়ে নিতে বলছেন।
বাসটা যাচ্ছে। সোনা এত অন্যমনস্ক হয়ে গেছিল যে সে কতদূর চলে এসেছে জানে না। সে বার বার কণ্ডাক্টারকে মনে করিয়ে দিচ্ছে—কে, জি, ডক। তিন নম্বর গেট। সে সেখানে নামবে। তাকে বেশিদূর নিয়ে গেলে সে চিনে ফিরে আসতে পারবে না। পকেটে তার এই বাসভাড়াই সম্বল। তার আর কিছু নেই। এবং এজন্য সোনার বার বারই মনে হচ্ছে সে বড় অকিঞ্চিৎকর মানুষ। তার কথা কণ্ডাক্টার মনে নাও রাখতে পারে। মনে না রাখলে সে খুব বিপদে পড়ে যাবে।
সহসা মনে হল, সোনার বাসের লোকগুলি ওর প্রতি খুব দয়ালু হয়ে উঠেছে। বুড়ো মতো একজন লোক বলল, এখনো অনেক দূর। তুমি বোসো। ঠিক তোমাকে নামিয়ে দেবে। তখন ওর মনে হল তবে বুঝি বেশ দূরই হবে। সে এক ঘুম ঘুমিয়ে নিতে পারে। সে বেশ চুপচাপ বসে এবার জানালার পাশের সব দালানকোঠা লাইটপোস্ট এবং রেলব্রীজ দেখতে দেখতে ভাবল এই শহরেই কোথাও অমলা কমলা থাকে। সে একবার দেখা করবে ওদের সঙ্গে। সে একটা চিঠি লিখবে, কোনওদিন সে কাউকে চিঠি দেয়নি। সে জাহাজে যখন চড়ে বসবে তখন সবাইকে চিঠি লিখবে। লিখবে, অমলা আমি বাংলাদেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছি। অথবা যদি সে অমলার সঙ্গে দেখা করতে যায়, ওকে চিনতে নাও পারে। সে কত বড় হয়ে গেছে। বরং সে চিঠিই লিখবে। সে কী কাজ নিয়ে যাচ্ছে জাহাজে তা লিখতে পারবে না। কাজটার কথা লিখতে ওর ভারি লজ্জা লাগবে।
এমন সময় কণ্ডাক্টারের গলা শুনতে পেল সোনা। এই যে কে নামবে কে, জি, ডকে। তিন নম্বর গেটে তুমি নামবে বলেছিলে? বলে কণ্ডাক্টর সোনার দিকে তাকাল। আশ্চর্য সোনা! সে এত তাড়াতাড়ি এসে পড়বে বুঝতে পারেনি। বেশ সে শহরের মানুষজন, রেলব্রীজ দেখছিল। ওর শীত করছিল না তেমন। সে ট্রেনিংশিপের সেকেণ্ড অফিসারের কাছে একটা চিঠি নিয়ে যাচ্ছে। এবং চিঠিটা দেখলেই ওকে ডেকে পাঠাবেন তিনি। কড়া মেজাজের মানুষ, ধমক দিয়ে কথা বলার অভ্যাস। এবং এমন সব নিষ্ঠুর ঘটনার সংবাদ সে রাখে যা মনে হলে শরীরের শীতটা বাড়ে। সে বাস থেকে নেমেই আবার কাঁপতে থাকল। গেটের মুখে দু’জন সিনিয়র রেটিঙস্। সামনে মাঠ এবং দূরে ক্রেন,জেটি, জাহাজের আগিল তিমিমাছের পেটের মতো। সে দাঁড়িয়ে ভালো করে দেখে নিল সব। গেটে লেখা, ট্রেনিংশিপ ভদ্রা। নুড়ি-বিছানো পথ। দু’পাশে ফুলের বাগান, তারপর জাহাজের জেটিতে ছোট মাঠ এবং নরম দুর্বা ঘাস। খুব মসৃণ, তার পাশে সোজা রাস্তা লকগেটের দিকে চলে গেছে। ফল ইনে সে কিছু নতুন রেটিঙস্ দাঁড়িয়ে আছে দেখতে পেল। পনের দিন পর পর একটা করে দল আসে। এই দিনেই সে এসেছে। ওর যতই এখন শীত করুক হাতের চিঠিটা সেকেণ্ড অফিসারের কাছে পৌঁছে দিতেই হবে। আর যতক্ষণ তিনি ডেকে তার সঙ্গে কথা না বলছেন ততক্ষণ শরীর থেকে শীত যাবে না। সে রেটিঙদের কাছে চিঠিটা দিল। অনুমতি না পেলে ভিতরে ঢুকতে পারবে না।
চিঠি নিয়ে ওদের একজন ডাবল মার্চ করে জাহাজের দিকে চলে গেল। সে ঠিকমতো পৌঁছে গেছে। সে যত কঠিন ভেবেছিল এখানে আসা, ঠিক ততটা কিঠন নয়। তার বড় ইচ্ছা করছিল গেটের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা রেটিঙদের সঙ্গে গল্প করতে। চিঠিটা পৌঁছে গেলেই তাকে ডেকে পাঠাবে। তার নাম লিস্ট করে নেবে। যারা তখন ফল-ইনে দাঁড়িয়ে আছে তাদের সঙ্গে দাঁড়াতে বলবে। দাঁড়াবার আগে যা যা শুনে এসেছে কতটা তা ঠিক বড় জানার ইচ্ছা তার। জাহাজের মাস্তুলে নিশান উড়ছে। এবং সে এখানে দাঁড়িয়েই দেখল মাস্তুলের মাথায় একটা কাক বসে আছে।
সে ভিতরে ঢুকে গেলে কাকটা ওর মাথার উপর কা-কা করে ডাকল। ওর ভিতরের শীতটা এবার আরও বেড়ে গেল। ওর দাঁত ঠকঠক করে কাঁপছে। ঠাণ্ডা বাতাস এত বেশি জোরে বইছে যে, সে বেশিক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না। রোদে যেন কোনও তাপ উত্তাপ নেই। মরা রোদের ভিতর ওর চোখদুটো আরও মরা দেখাচ্ছে। যারা ডেকের উপর দাঁড়িয়ে অথবা টুইন ডেকে ডিউটি করছে তাদের শরীরে শুধু গেঞ্জি। ওরা শীতে কাঁপছে না। ওদের দেখে সোনা এতক্ষণে বুঝতে পারছে সে শীতে কাঁপছে না, ভয়ে কাঁপছে। তাকে কারা যেন বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে, ঠিক সেই দালানকোঠার ভিতর বলির মোষটার মতো। সে দেখতে পেল চোখের সামনে ঢাকঢোল বাজছে, ধূপধুনোর গন্ধ উঠেছে, চোখ জ্বালা করছে। কচি মোষটাকে টেনে টেনে নিয়ে আসছে। সকাল থেকে বড় শীতে কাপছিল মোষটা।
বিউগিল বাজলে সোনা টের পেল সেও ফল-ইনে দাঁড়িয়ে গেছে। ডেকের উপর কাপ্তান। সামনে চিফ, সেকেণ্ড এবং থার্ড অফিসার। সেকেণ্ড অফিসার দু’কদম সামনে এসে কমাণ্ড দিচ্ছেন।
সোনা শুনতে পেল, ঠিক সেই পুরোহিতের মতো গলা, জোরে জোরে মন্ত্র উচ্চারণের মতো হেঁকে ওঠা—ট্রেনিজ বলে তিনি যেন দম নিলেন, তারপর সবার সঙ্গে সোনা অ্যাটেনশান হয়ে গেল। ঠিক সেই কল লাগানো পুতুলের মতো। ওর যা কিছু নিজস্ব, এই যেমন ওর ইচ্ছা, ভালোবাসা এবং বড় হওয়ার স্বাধীন আকাঙ্ক্ষা সব সে ঝেড়ে ফেলে এখন ওরা যা যা বলবে তাই করবে। যদি ওকে ওরা ক্লাউন সাজিয়ে ছেড়ে দেয় সে সারাজীবন একটা ক্লাউন হয়েই থাকবে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি আবার ডেকের ওপর হেঁকে উঠলেন, ট্রেনিজ, দি থার্টিফোর ব্যাচ—স্ট্যাণ্ড অ্যাট ইজ। সোনা সহজ হয়ে দাঁড়াতে পেরে একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।
বোট-ডেকের ওপাশে সূর্য কিরণ দিচ্ছে। জাহাজের ওপাশে বড় বড় সব গাদা বোট। এবং দূরে ওপারের জেটিতে ক্ল্যানলাইনের জাহাজ। জাহাজের মাস্তুল পার হলে জেটি এবং শেড আর বড় বড় সব ক্রেনগুলি দৈত্যের মতো দাঁড়িয়ে লম্বা ছায়া ফেলেছে জেটির জলে। অথচ এরই ভিতর সে একটা ঘুঘু পাখির ডাক শুনতে পেল। কোথাও এখানে তবে ঝোপজঙ্গল আছে যেখানে এই শীতের সময়েও ঘুঘু পাখি বাস করতে পারে। ঘুঘুপাখির ডাক শুনলেই বাংলাদেশের কথা মনে হয়। ফতিমার কথা মনে হয়। প্রিয় অর্জুন গাছটার নিচে কেউ দাঁড়িয়ে আছে মনে হয়। গাছটা একাকী নিঃসম্বল মানুষের মতো দাঁড়িয়ে আছে। সে নেই, জ্যাঠামশাই নেই। ফতিমা শহরে থাকে। ফতিমা, জ্যাঠামশাই না থাকলে গাছটারও থাকার কোনও মানে নেই। কিন্তু সেই গাছটার নিচে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। অস্পষ্ট মুখ ধীরে ধীরে স্পষ্ট হলে দেখল ঈশম দাঁড়িয়ে আছে। সে ঘুরেফিরে আবার তার তরমুজের জমিতে নেমে যাচ্ছে। সে এই গাছ এবং তরমুজের জমি ফেলে কোথাও গিয়ে শান্তি পাচ্ছে না। আর এমন সময়ই সে শুনতে পেল, ট্রেনিজ, দি থার্টিফোর স্ট্যাণ্ড ইজি।
ওরা ফল-ইনে দাঁড়িয়ে হাত-পা হেলাতে পারছে। এমনকি ওরা এখন পরস্পর গা চুলকেও নিতে পারে। সহজ হয়ে দাঁড়াতে পারায় সোনা কেমন সাহস পেল। শীতের সূর্য জাহাজের ওপাশ থেকে মাথার ওপর এপাশে উঠে আসছে। শীতের সূর্য ওকে উত্তাপ দিচ্ছে। সে বাঁচতে পারবে এই উত্তাপে। সে এখানে হাতখরচ পাবে সাত টাকা। দু’বেলা পেট ভরে খেতে পাবে। এটা যে ওর কাছে কী মহার্ঘ ব্যাপার, ক্ষুধায় সে কাতর এবং দুপুর হলেই বোট-ডেকে বড় বড় কলাইকরা থালাতে ভেড়ার মাংস আর ভাত। সূর্যটা যত তাড়াতাড়ি মাথার ওপর উঠে আসবে তত তাড়াতাড়ি সে খেতে পাবে। সে কাজের ফাঁকে ফাঁকে তাই সূর্য দেখে। সূর্য দেখলে কী হবে, সে তো জানে তাদের এখন নিয়ে যাওয়া হবে বোট-ডেকে। তাদের ডেকের কাঠে ক্রমাগত দুঘণ্টা হলিস্টোন মারতে হবে। এই দু’ঘণ্টায় কেউ অজ্ঞান হয়ে গেলে বিদায় করে দেওয়া হবে, তাকে ভেড়ার মাংস-ভাত খেতে দেওয়া হবে না। এমন ভাবতে সোনার বুক গলা শুকিয়ে গেল। সে আজ খেতে না পেলে মরে যাবে। খাবারের জন্য সে আর যাই হোক অজ্ঞান কিছুতেই হবে না।
বোট-ডেকে সে সবার সঙ্গে উঠে গেল। সারাটা ডেক কারা জল মেরে গেছে। লাইট-বোটের পাশে দু’জন সিনিয়র ট্রেনিজ ওদের উঠে আসতে দেখে ভারি মজা পাচ্ছিল। ওদের হাতে হোস পাইপ। ওদের আরও চার-পাঁচজন জটলা করছে মেসরুমের পাশে। ওদের হাতে বালি। ওরা ডেকের কাঠে বালি ছড়িয়ে যাচ্ছে। যারা নতুন এসেছে, সারি সারি তারা হলিস্টোন মারতে বসে গেল। সাদা রঙের চৌকো পাথর। কিভাবে বসবে, কিভাবে দু’হাতে হলিস্টোন ধরবে, সব একজন সিনিয়র ট্রেনি সামনে বসে দেখিয়ে দিচ্ছে। বসার এদিক-ওদিক হলে পিছন থেকে পাছায় লাথি খেতে হবে। সোনা সব ভাল করে লক্ষ করছে। সে দু’পায়ের ওপর ভর করে আলগা হয়ে বসল। দুহাতে চেপে হলিস্টোন ধরে রাখল। এমন ঘষামাজা ডেক, ফের ঘষতে হবে। কাঠ পাতলা হয়ে গেছে ঘষতে ঘষতে। কোথাও ছোবড়া বের হয়ে পড়েছে। তবু ঘষতে হবে। উপুড় হয়ে বাটনা বাটার মতো ক্রমান্বয়ে ঘষা, ডেক ঘষে যাওয়া। জল মারছে হোস পাইপে। জলে ওদের ভিজিয়ে দিচ্ছে। বালি ছড়িয়ে দিচ্ছে। ঘষে ঘষে হাত-পা গরম। তারপর দু’হাতে পায়ে যেন খিল ধরে আসছে। সেকেণ্ড অফিসার পোর্টহোলে চোখ রেখে সব দেখছেন। হলিস্টোন মারতে মারতে কে হেলে যাচ্ছে, কার হাত শিথিল হয়ে যাচ্ছে, কার হাতে ফোসকা পড়ে ছাল চামড়া উঠে যাচ্ছে, দেখে আরও চালিয়ে যাবার জন্য অর্থাৎ যতক্ষণ ওরা বাপরে মারে ডাক না ছোটাবে, যতক্ষণ দু-কষে ফেনা উঠে না যাবে, এবং কেউ কেউ শরীর খিল মেরে অজ্ঞান হয়ে না যাবে ততক্ষণ চালিয়ে যাবে। সিনিয়র ট্রেনিদের এটা একটা বড়দিনের উৎসবের মতো। প্রথম দিনে ওরাও এমন একটা দৃশ্যের ভিতর পড়ে গেছিল। এখন ওরা সোনাদের দেখে মজা পাচ্ছে। চারপাশে ঘসঘস শব্দ। সোনা কানে এখন কিছু শুনতে পাচ্ছে না। পাশের ছেলেটা চিৎ হয়ে পড়ে আছে। কেউ আসছে না। সে উঠে ওকে ধরবে ভাবল, কিন্তু সে জানে সহসা উঠে দাঁড়ালেই পড়ে যাবে। ঠিক উপনয়নের দিনের মতো—নানারকমের মন্ত্র উচ্চারণের ভিতর চারপাশে নানারকমের মজা। মানুষের শরীরে নতুন এক পরিমণ্ডল তৈরি করা। সোনা তুমি এক মানুষ, তোমার এইদিনে মানুষের জন্য আর মায়া থাকছে না, তোমার হাতে ফোসকা পড়ে দগদগে ঘা হয়ে গেছে। হাত খুলে আর দেখো না। দেখলে তুমিও অজ্ঞান হয়ে যাবে। কিন্তু হলে কী হবে, সোনা তো এসব পারে না। সে ছেলেটাকে ধরে তুলতে গেল। আর আশ্চর্য, সে দেখলে দু’জন রেটিঙস্ ওর মুখের ওপর হোস পাইপে জল মারছে। তাকে প্রায় লাথি মেরে পাশে ঠেলে ওরা আরও মজা দেখার জন্য ছেলেটার মুখে হোস পাইপ ছেড়ে দিল। এমন নিষ্ঠুর ঘটনায় সোনার চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছা হল। কিন্তু পারল না। আর কিছুক্ষণ সময় পার করে দিতে পারলেই বোট-ডেকে বসে ভেড়ার মাংস-ভাত। কলাইকরা থালায় সে ভেড়ার মাংস-ভাত খাবে। সে কিছুতেই প্রতিবাদ করতে পারল না। চোখের উপর দেখল, চ্যাঙদোলা করে ওরা ছেলেটাকে নিয়ে যাচ্ছে। টেনে হিঁচড়ে বোট-ডেকের উপর দিয়ে নিয়ে গেলে সোনা চোখ ফিরিয়ে নিল। ছেলেটার হাতে-পায়ের চামড়া ছড়ে যাচ্ছে, তার দেখতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল।
সঙ্গে সঙ্গে হুইসল বেজে উঠলে সবাই দাঁড়িয়ে পড়ল। হলিস্টোন শেষ। কেউ আর ঠিকমতো দাঁড়াতে পারছে না। ওরা টলছে। সোনা দু’পায়ের উপর শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। সে কিছুতেই পড়ে যাবে না। পড়ে গেলেই ওরা ওকে চ্যাঙদোলা করে নিয়ে যাবে। যতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে—সে মানুষ, পড়ে গেলেই মানুষ না। তাকে নিয়ে যা খুশি করা। সেকেণ্ড অফিসার আসছেন। বুটের শব্দে সোনা চোখ তুলে তাকাল। পরনে সাদা হাফ প্যান্ট সাদা হাফশার্ট এবং মাথায় জাহাজী টুপি। চোখমুখ কী ভীষণ কঠিন! তিনি যে বাঙালী, তিনি বাংলা ভাষায় কথা বলেন কখনও কখনও, এখন মুখ দেখে তা কিছুতেই বোঝা গেল না। সব কমাণ্ড তাঁর হিন্দিতে, সব কথা হিন্দিতে। সোনার মনে হল তিনি রাতে শুয়ে স্বপ্ন দেখেন হিন্দিতে। তিনি যে পোর্টহোলে মুখ রেখে প্রতিটি রেটিঙসের ওপর কড়া নজর রেখেছিলেন, এবং যাদের ওপর কোনও সংশয় আছে তাঁর, তাদের কাছে গিয়েই দাঁড়াচ্ছেন, তারা তা বুঝতে পারছে না। সূর্য যখন মাথার উপরে উঠে গেছে—আর তখন তিনি বেশি দেরি করবেন না। ছেড়ে দেবেন এবার। হাতে ফোসকা গলে রক্ত পড়ছে, ক্ষুধার জ্বালায় সোনা তা পর্যন্ত টের পাচ্ছে না। যারা হাতে এখন ব্যান্ডেজ বেঁধে দিচ্ছে সে তাদের কিছু বলবে ভাবল। কিন্তু বলতে পারল না। সেকেণ্ড অফিসার এবার ওর দিকে আসছেন।
সেকেণ্ড অফিসারের কঠিন মুখ দেখে সোনা বুঝি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। ভয়ে সে কিছুতেই তাকাতে পারছিল না। তিনি এসে ওর সামনে দু’পা ফাঁক করে দাঁড়ালেন। সে এবার বুঝি সত্যি পড়ে যাবে। সে বলল, ঈশ্বর আপনি আমাকে আর একটু শক্তি দিন। এই দুপুর পর্যন্ত। পড়ে গেলে আমার ভেড়ার মাংস-ভাত আর খাওয়া হবে না। শীতের রোদ, ক্রমান্বয়ে দু’ঘণ্টা হলিস্টোন, সোনার মুখে যে আশ্চর্য এক সুষমা আছে তা নষ্ট করতে পারেনি। ক্লান্ত অবসন্ন মুখে তার কোথায় যে এক আশ্চর্য দীপ্তি! কেন যে সেকেণ্ড অফিসার এদিকে আসছেন, কিভাবে যে সোনা তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে এমন ভাবতেই তিনি সোনার শরীর টিপে টিপে দেখলেন। প্রায় হাট থেকে গাই গরু কেনার মতো খোঁচা দিয়ে দেখা। যেন হাত-পা টিপে টিপে পরীক্ষা করলেন সমুদ্রের ভয়ঙ্কর ঝড়, সারেঙের অত্যাচার এবং সফরের কঠিন নিঃসঙ্গতা সে সহ্য করতে পারবে কি-না। না পারলে এক্ষুনি বিদায় করতে হবে। সুন্দর চোখমুখ দেখলেই সেকেণ্ড অফিসারের এমন ভয় হয়। তারপর সহসা ভয় পাইয়ে দেবার মতো চিৎকার করে বললেন, অ্যাটেনশান। সোনার দিকে তাকিয়ে বললেন, ঠিকসে খাড়া রহো। হিলতা কিও?
সোনা সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে থাকল।
—তোমার নাম কেয়া হ্যায়?
কাকে বলছে সোনা বুঝতে পারছে না। সে তো সামনের দিকে তাকিয়ে আছে, সে কী করে বুঝবে সেকেণ্ড অফিসার তার দিকে তাকিয়ে কথা বলছেন।
এবার তিনি ওর চুল টেনে বললেন, তোমার নাম কেয়া হ্যায়?
সে সামনের দিকে তাকিয়েই বলল, শ্রী অতীশ দীপঙ্কর ভৌমিক।
—মজুমদারসাহেব কাহাসে এক জংলি আদমি ভেজারে! বলেই তিনি সোনার গালে ঠাস ঠাস দু’চড় বসিয়ে বললেন, ঠিকসে বাত বলনে হোগা।
সোনার মনে হল দাঁত ক’টা উড়ে গেছে। দাঁতের কষ চিরে যে রক্ত পড়ছে সেটা বোঝা যাচ্ছে। রক্তের নোনতা স্বাদ লালার সঙ্গে জিভ দিয়ে সে চেটে নিল। পেটে তবু যা হোক কিছু যাচ্ছে। সে কাঁদতে পারত আজ। অথচ অদ্ভুত, ওর কান্না পাচ্ছে না। হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। সে অ্যাটেনশান হয়ে আছে। গালে নিজের হাত তুলে দেখতে পারছে না, ক’টা দাঁত আছে ক’টা গেছে। কারণ গোটা মুখ কেমন ভোঁতা মেরে গেছে। সে কিছুতেই বুঝতে পারছে না শুধু নোনতা স্বাদে সে বুঝতে পারছে রক্ত বের হচ্ছে। ক্ষুধার সময় নিজের রক্ত চুষে খেতে মন্দ লাগছে না। সে নিজের রক্ত চেটে খেতে খেতে ভয়ঙ্কর সেই কঠিন মুখ দেখে ফের শীতল হয়ে গেল। কেন যে তিনি তাকে এমন কষ্ট দিচ্ছেন, সে তো তার নাম ঠিকই বলেছে। সে এতদিন ধরে তার এই নাম জেনে এসেছে। এখানে এলে নতুন নামকরণ হয় কি-না সে এখন তা জানে না। জানলে সে এমন বলত না। যখন সে কারণ খুঁজে পাচ্ছিল না অথচ সেকেণ্ড অফিসার ওর কান টেনে সামনে পিছনে মাথা দোলাচ্ছেন তখন ওর বলতে ইচ্ছা হল স্যার, আমাকে যে নামেই ডাকুন, যে ভাবেই মারুন, আমি জাহাজ ছেড়ে যাচ্ছি না। আমি আর একটু বাদে ভেড়ার মাংস-ভাত খাবই।
তিনি কান ছেড়ে দেবার সময় বললেন, বাত বা পিছু মে স্যার বলনে হোগা, মেরা নাম শ্রী অতীশ দীপঙ্কর ভৌমিক স্যার, বলনে হোগা।
সোনা সোজা দাঁড়িয়ে বলল, মেরা নাম শ্রী অতীশ দীপঙ্কর ভৌমিক স্যার।
—ঠিক হ্যায়। তারপর তিনি সোনার পা থেকে মাথা পর্যন্ত ভালো করে দেখলেন। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন।—জাহাজ মে বহুত তকলিফ হায়। জাহাজকা নকরি বহুত খতরনাক হ্যায়। সারেঙ লোক দুশমনি করেগা। বহুত লেড়কা লোক আতা হ্যায়, ট্রেনিং লেতা হ্যায়, এক দো সফর বাদ ভাগতা হ্যায়। তুমকো ভি ভাগনা পড়ে গা!
—না স্যার, আমি ভাগব না।
—সাকগে তুম?
—পারব স্যার। সোনা আর কিছু না বলে সোজা তাকিয়ে থাকল। তিনি চলে যাচ্ছেন। সোনার এত কষ্টের ভিতরও মনে হল যাক, তবে এত দিনে একটা তার হিল্লে হয়ে গেল। কিন্তু একি! তিনি যে আবার ফিরে আসছেন! প্রায় কুইক মার্চের মতো মনে হচ্ছে। এসেই মুখের ওপর শক্ত হয়ে বললেন, তুম বিফ খানে সকতা?
বিফ! আমি বিফ খাব কেন! আমি হিন্দুর ছেলে, হিন্দুস্থানে চলে এসেছি। আমি আবার বিফ খাব কেন! যারা পাকিস্তানে আছে তারা বিফ খাবে। বিফের ভয়ে আমার জ্যাঠামশাই গঙ্গার পাড়ে ঝোপজঙ্গলে বাড়ি করেছেন। আমার বাবা মাঝে মাঝে আসেন। বড় জ্যেঠিমা খেতে না পেলে চিঠি নিয়ে বসে থাকেন, ছোটকাকা চলে গেছেন বাড়ি ছেড়ে, এত হবার পর হিন্দুর ছেলে হয়ে বিফ খাব, সে কি করে হয়! ভাবতে ভাবতে সোনা ঢোক গিলে ফেলল। সোনার এত খিদে যে বিফ মটন সব এক হয়ে যাচ্ছে। তবু এক আজন্ম সংস্কার, তীব্র ঘৃণাবোধ সারা শরীরে দগদগে ঘা হয়ে ফুটে উঠল। তীক্ষ্ণ যন্ত্রণায় শরীর নীল হয়ে যাচ্ছে। সে এবার মরে যাবে যেন। চারপাশে ঋষিপুরুষেরা দাঁড়িয়ে আছেন। কী সব মন্ত্রগাথা তাঁরা উচ্চারণ করে চলেছেন। যেন হোমের কাঠ থেকে এক পবিত্র গন্ধ উঠে সারা শরীরময় ভেসে বেড়াচ্ছে। ওর চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছা হল, বলতে ইচ্ছা হল, না না আমি সব পারব। এটা পারব না। আমাকে আমার জন্ম থেকে আমার বাবা মা, আমার পূর্বপুরুষ, মাটি ফুল ফল এক আশ্চর্য পরিমণ্ডলে মানুষ করেছেন, আমি সব পারি স্যার, কিন্তু সেই পরিমণ্ডল ভেঙে দিতে পারি না। ভেঙে দিলে আমার আর কিছু থাকে না।
এত দেরি দেখে তিনি ক্ষেপে গেলেন।—জাহাজ মে নোকরি করনেসে বিফ তুমকো খানেই হোগা। বোল, সাকোগে কী নেহি?
আশ্চর্যভাবে সোনার সমনে মায়ের মুখ ভেসে উঠল। শীতের রাতে মা কুপি জ্বালিয়ে বাবার প্রত্যাশায় বসে আছেন। উঠোনে সেই আবহমান কালের সাদা জ্যোৎস্না। উনুনে শুধু জল সেদ্ধ হচ্ছে। বাবা এলেই দু’মুঠো অন্ন সবার পাতে। কী উদগ্রীব চোখমুখ ছোট ছোট ভাইবোনদের। সে তার স্থৈর্য হারিয়ে ফেলছে। মা তার অন্নহীন। ভাইবোনের শুকনো চোখমুখ ভেসে উঠলে, সে বলল, আমি পারব স্যার। সে বলতে বলতে মাথা নিচু করে ফেলল। সেকেণ্ড অফিসার টের পাচ্ছেন ছেলেটি ওর সামনে দাঁড়িয়ে মাথা নিচু করে, এই প্রথম এত যন্ত্রণার পর কাঁদছে। ওর এ সময় সান্ত্বনা দেবার কোনও ভাষা থাকে না। তিনি যেমন বার বার কুইক মার্চ করে যান আসেন, আজও তিনি তেমনি কুইক মার্চ করে চলে গেলেন। তিনি যেন এখন বলতে বলতে যাচ্ছেন, আমার পিতা অঘোরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পিতামহের নাম হরিবিলাস চট্টোপাধ্যায়, তস্য পিতামহের নাম যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়। তুমি চোখের জল ফেলে আমাকে কী ভয় দেখাচ্ছ হে ছোকরা!
আহা! তারপর শীতের রোদে ভেড়ার মাংস গরম ভাত। ডেকের উপর বসে পেট ভরে খাওয়া। মাথার উপর খোলা আকাশ। সামনে নদী। ওপারের কলকারখানা, কলের চিমনি এবং নীল আকাশ। কত সব পাখি মোহনার দিকে উড়ে যাচ্ছে। সোনা খেতে খেতে এই সব পাখি দেখল, ওরা উড়ে যাচ্ছে। ট্রেনিং শেষ হয়ে গেলে সেও চলে যাবে, জাহাজে সে বাংলাদেশ ছেড়ে সমুদ্রে চলে যাবে। কবে ফিরবে সে জানে না। আর এই বাংলাদেশে সে ফিরতে পারবে কি-না তাও জানে না। ওর মনটা খেতে খেতে ভারি হয়ে গেল। মার জন্য, ছোট ছোট ভাইবোনদের জন্য ওর কষ্ট হতে থাকল। সে কলাইকরা থালা মগ ধুয়ে বাংকে রেখে এল। তারপর মাস্তুলের নিচে শীতের দুপুরে শুয়ে পড়ল। ওর এখন বিশ্রাম। ওর ভীষণ ঘুম পাচ্ছে। পেট পুরে খেলেই শীতের দুপুরে ওর বড় ঘুম পায়।
সোনা যখন মাস্তুলের নিচে শুয়ে ঘুমোচ্ছে, যখন বাংলাদেশের আকাশ নীল, মানুষেরা শীতের রোদে উত্তাপ নিচ্ছে তখন সামসুদ্দিন দেখল ডায়াসে বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা কমিটির আহ্বায়ক আবদুল মতিন উঠে দাঁড়িয়েছেন। সামসুদ্দিন দেখছে সকাল থেকে অগণিত ছাত্র সমুদ্র তরঙ্গের মতো ছুটে আসছে। ওরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ঢুকে যাচ্ছে। পুলিশের ব্যারিকেড তুচ্ছ করে ওরা ঝাঁপিয়ে পড়ছে ভিতরে। সে দেখছিল। ওর গর্বের অন্ত ছিল না। অজস্র পলাশ গাছ যদি কোথাও থাকে তার লাল পাপড়ি, ওর মনে হল ওরা পলাশের পাপড়িই হবে-নতুন আকাশ এমন রাঙা হতো না, যেন লক্ষ লক্ষ পলাশের পাপড়ি বাংলাদেশের আকাশ নিমেষে ঢেকে দিচ্ছে—আকাশটা রাঙা হয়ে গেলে, মতিনসাহেব বলে উঠলেন, ভাইসাব, ফ্যাসিস্ট লীগ সরকার আমাদের দাবি বানচাল করে দেবার জন্য ১৪৪ ধারা জারি করেছে।
সামসুদ্দিনের সাদা রঙের শালের উপর নানারকম প্রজাপতি আঁকা। সে শালটা দিয়ে মুখ মুছল। এই শীতের দুপুরে সে নেমে যাচ্ছে। সে শালটা ঝেড়ে কাঁধে ফেলে রাখলে মনে হল প্রজাপতিগুলি উড়ে গেছে। প্রজাপতি উড়ে গেলে আর কিছু থাকে না। আজ এই দিনে মাঠে মাঠে যত ফুল আছে, সব ফুল থেকে প্রজাপতি উড়ে যাচ্ছে। এমনকি জালালির কবরে সে যে প্রজাপতি উড়িয়ে দেবে বলেছিল, পুলিশের অত্যাচার দেখে মনে হচ্ছে তাও সে আর বুঝি পারবে না। ফলে কবর থেকে জালালির মুখ ভেসে ভেসে চলে আসছে। জালালি যেন তাকিয়ে আছে অথবা সেই মহারাত্রির ঘটনা এই প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে হুবহু মনে পড়ে গেল। জালালি ক্ষুধায় হাঁসটার মাংস চিবুচ্ছে। কড়মড় করে হাঁসের হাড় গিলে ফেলছে। কী নিষ্ঠুর ছিল সেই ক্ষুধার্ত মুখের ছবি! এবং পেট ভরে গেলে জালালির মনোরম মুখ – সে এই বাংলাদেশে এমন সুন্দর মনোরম মুখের ছবি আঁকতে চেয়েছে। পেট ভরে গেলেই মানুষের আর দুঃখ থাকে না। আল্লার দুনিয়ায় বেঁচে থাকতে ভালো লাগে। সে যে একটা শপথপত্র রেখে দিয়েছিল জালালির কবরে, সেই শপথপত্রটাও যেন কবরের নিচ থেকে উঠে এসে একটা ফেস্টুন হয়ে গেছে বাতাসে পতপত করে উড়ছে। সে যা চেয়েছিল তা করতে পারে নি। কারা এসে সব উল্টে পাল্টে দিল। সে আর মুসলিম লীগ জিন্দাবাদ, এমন বলতে সাহস পায় না। কত সব নীচ হীন স্বার্থপর এসে ওর যে শপথপত্র ছিল জালালির কবরে, ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে। সে মতিনসাহেবের গলার সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলে উঠল, ফ্যাসিস্ট লীগ সরকার আমার আপনার মুখের ভাষা কাইড়া নিতে চায়।
সামসুদ্দিন এই বলে আরম্ভ করল। হাজার হাজার তরুণ, যুবা উন্মুখ হয়ে শুনছে। মহারণে যাবার আগে এই কঠিন প্রতিজ্ঞার কথা ওরা শুনে যাচ্ছে। ওরা কেউ কোনও কথা বলছে না। বাংলাদেশ আমাদেরই বাংলাদেশ, ভাষা আমাদের বাংলা ভাষা, বাংলার জল, বাংলার মাটি আমাদেরই নিকনো ঘরের ছবি, তাকে ফেলে যাব কোথা! তারে ছাইড়া দিলে থাকেডা কি!
বুঝি ঈশমের হাতে সে এক মুশকিলাসানের লম্ফ দেখতে পেল। কেন যে এতদিন পর ঈশমচাচার কথা ওর মনে এল সে জানে না। যেন সেই ফকিরসাব হাতে মুশকিলাসানের লম্ফ-হেঁটে হেঁটে যাচ্ছেন। তাঁর পিছনে কে যেন বার বার তাঁকে অনুসরণ করতে বলছে। সে এতদিন ঈশমচাচার কোন খোঁজই রাখেনি। ঠাকুর বাড়ির সবাই চলে গেছে—তারপর চাচার কী হল, সে কোথায়, সে জানে না। সে জানে না ঈশম অন্নহীন ভূমিহীন। ঈশম হয়তো গভীর রাতে তরমুজের জমিতে ফিরে আসতে চায়। ঈশম হয়তো দেখতে পায় তখন তার নীলকণ্ঠ পাখিরা সব উড়ে গেছে কোথাও। হাতের তালিতে আর ওরা ফিরে আসবে না। ঠাকুরবাড়ির মানুষদের ও-পারে বুঝি এতদিনে সেই পাখিটার খোঁজ মিলে গেছে। না মিলে গেলে ওরা আবার নদী বন মাঠ পার হয়ে ছুটবে। সামসুদ্দিনের মনে হয়েছিল, তার পাখি আকাশে ওড়ে না, নদীর পাড়ে বসে থাকে। দেশভাগের পর পরই সে ভেবেছিল, তবে বুঝি এবারে সব মিলে গেল—কিন্তু হায়, যত দিন যায়—সে দেখতে পায় সংসারে সবাই পাখিটাকে ছেড়ে দিয়ে বসে থাকে—আবার খুঁজে বেড়ায়। পেলে মনে হয় পাখি মিলে গেছে, দুদিন যেতে না যেতেই মনে হয় পাখিটা আর নীলরঙের নয়, কেমন অন্য রঙ হয়ে গেছে। সে বলল, এটা আমাদের জীবন-মরণের শামিল। থামলে চলবে না। আমাদের সংগ্রাম চলছে, চলবে।
সামসুদ্দিন একটু দম নিল।
বড় রাস্তায় সব পুলিশের গাড়ি টহল দিচ্ছে! দোকানপাট বন্ধ। সারা শহর থমথম করছে। পুলিশেরা মাঝে মাঝে কোথাও টিয়ার গ্যাসের শেল ফাটাচ্ছে। অথচ বার বার কেন যে একজন মানুষ, আজ সবচেয়ে বেশি তাকে ইশারায় ডাকছে বুঝতে পারছে না। সে এবার বলতে চাইল, আমি আবার যাব আপনার কাছে। তার আজ সবার কথা মনে হচ্ছে। সেই ছোট ছেলে সোনার কথা মনে হচ্ছে। সে যখন সোনার মতো ছিল তখন ঈশমচাচা গভীর রাতে এসে ডাকতেন, সামু ঘুমাইলি?
—না ঘুমাই নাই।
—তর লাইগা আনছি।
—কী আনছেন চাচা? সে ঘুম থেকে উঠে বাইরে আসত। দশমীর বাজনা বাজছে না। বিসর্জন হয়ে গেছে ঠাকুরের। দশমীর মেলা থেকে সে ফিরে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল টেরই পায়নি। উঠে দেখত চাচা উঠোনে দাঁড়িয়ে আছে। হাতে ঝকঝকে টিনের তলোয়ার।
সামু ঝকঝকে তলোয়ার দেখে চাচাকে জড়িয়ে ধরত। সে দুগ্গাঠাকুরের তলোয়ারটা বালিশের নিচে রেখে দিত। সকাল হলে সে রাজা সেজে বাড়ি বাড়ি ঘুরে আসত. মাথায় তার আমপাতার মুকুট।
সামুর মনে হল ওর সেই আম-জামপাতার মুকুট এখনও কে যেন মাথায় তার পরিয়ে রেখেছে। সে যতই হিন্দুবিদ্বেষের কথা বলুক মাথার আম-জামপাতার মুকুট সে ফেলে দিতে পারেনি। ফেলে দিতে গেলেই দেখেছে ভিতরটা তার হাহাকার করে উঠেছে। মালতীর কথা মনে আসতেই আবেগে সে বলে উঠল, আজ আমাদের আন্দোলনের দিন, মায়ের ঋণ শোধ করার দিন। আমাদের মা, বাংলামার চেয়ে বড় কিছু নেই। যতদিন ঋণ শোধ না হবে, ততদিন আমাদের রেহাই নেই।
ধীরে ধীরে ছাত্ররা এবার বের হয়ে গেল। ওরা বন্দুকের নলের সামনে গিয়ে দাঁড়াবে। আমাদের মা, বাংলা মার চেয়ে বড় কিছু নেই। দশজন করে এক একটা দল এগিয়ে যাচ্ছে। কী শান্ত নীল আকাশ। মাথায় সবার আম-জামপাতার মুকুট, রাজার মকুট। মা তাদের যেন পরিয়ে দিয়েছেন। তারা যেতে যেতে গান গাইছে, ওগো মা জননী, আমাগো মুখের ভাষা কাইড়া নিতে চায়, আমরা কি করি!
সফিকুর দশজনের একটা দল নিয়ে হাঁটছে। হাতে পোস্টার। তাতে লেখা—চলো যাই চলো, যাই চলো যাই—চলো পদে পদে সত্যের ছন্দে, চলো দুর্জয় প্রাণের আনন্দে। কারও পোস্টারে অথবা কণ্ঠে লেখা—ওরা গুলি ছোড়ে এদেশের প্রাণে দেশের দাবিকে রোখে, ওদের ঘৃণ্য পদাঘাত এই বাঙালীর বুকে, ওরা এদেশের নয়, দেশের ভাগ্য ওরা করে বিক্রয়, ওরা মানুষের অন্নবস্ত্র শান্তি নিয়েছে কাড়ি, একুশে ফেব্রুআরি, একুশে ফেব্রুআরি। সব শেষে দোহারের মতো সফিকুর সবার সঙ্গে গায়, আমরা কি যে করি!
ফতিমা যাচ্ছে দশজনের একটা দল নিয়ে। ওদের শাড়িতে জমিনের রঙ সাদা, পাড়ের রঙ নীল। ওরা বুকে ব্যাজ এঁটে নিয়েছে—একুশে ফেব্রুআরি। শীতের রোদে ওরা এগিয়ে যাচ্ছে। তারাও গাইছে সমস্বরে—আমরা কি যে করি!
এ-ভাবে যাচ্ছে। একের পর এক দশজনের একটা দল বের হয়ে যাচ্ছে। হাতে নানা রঙের ফেস্টুন। মুখে গরিমা। তারা বন্দুকের নলের সামনে ধীর পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে। তারা বাংলার জল, বাংলার বায়ু বলতে বলতে চলে যাচ্ছে। শহরবাসীরা জানালা দরজা বন্ধ করে বসে রয়েছে। ভয়, কখন দাবানলের মতো বিদ্রোহী ছাত্ররা আগুন জ্বালিয়ে দেবে ব্যারাকে ব্যারাকে। ওরা শার্শির ফাঁকে দেখল, কী নির্ভীক ছাত্ররা! ছাত্ররা পুলিশ কর্ডনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, আর অনবরত গাইছে, আমরা কি যে করি!
আর এই কী করি, কী করি করতেই রাইফেল গর্জে উঠল। মেডিক্যাল কলেজের শেডের নিচে ছাত্ররা এসে জমায়েত হচ্ছিল—তখন এমন এক কাণ্ড। কাণ্ড আর কাকে বলে। মানুষেরা চোখ মেলে দৃশ্যটা দেখতে পর্যন্ত পারছে না। দরজা জানালা বন্ধ করে দিয়েছে। শার্শির ফাঁকটুকু পর্যন্ত রাখেনি। কি জানি ফাঁকে ফোকরে যদি গুলি ঢুকে যায়। দাঁতে দাঁত চেপে কে তখন বলে উঠল বেইমান। এমন হিং ছবির ভিতরও ওরা এগিয়ে যাচ্ছে, ওরা ওদের বুকের বল হারাচ্ছে না, ওরা গাইছে, আমরা কি যে করি! ওরা হাত তুলে যেন পারলে আকাশ থেকে সূর্য উপড়ে আনে—ওরা সমস্বরে বলছিল—আমাদের ভাষা, বাংলা ভাষা। রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।
ভাষা রক্তে তখন বাংলার ঘাস মাটি ফুল ভেসে যাচ্ছে। যা কিছু রঙ নীল অথবা সবুজ সবই কেমন লালে লাল হয়ে গেল। মনে হচ্ছে সারা আকাশটাই একটা শিমুলের গাছ, ডালে ডালে অজস্র লাল ফুল, ফুলের পাপড়ি এবার এই রাজপথে, মিনারে গম্বুজে ছড়িয়ে পড়বে। গ্রামে, মাঠে, শহরে, গঞ্জে বাংলার মানুষ আকাশে এতসব শিমূল ফুলের পাপড়ি উড়তে দেখে যেন হা-হুতাশ করছে—এ-ঋণ শোধিবে কে! এই যে হৃদয় ভেঙে টুকরো টুকরো –এ-ঋণ শোধিবে কে! কে মানুষ এমন আছে বলতে পারে, খামু দামু ঘরে যামু তাজা রক্ত মায়েরে দিমু। আর কি দিমু তোমারে, দিমু আমার জান প্রাণ। সফিকুর হাইকোর্টের সামনে তার জানপ্রাণ দিয়ে মায়ের সম্মান রক্ষা করেছে। ওর দু’হাতে শক্ত করে ধরা পোস্টার। সে পড়ে গেলে পোস্টারটা ওর নিচে না পড়ে যায়, মায়ের জন্য তার মাথার কাছে পাতা আছে আসন, সে মাথার কাছে বিছিয়ে রেখেছে পোস্টার—আমার মুখের ভাষা অরা কাইড়া নিতে চায়। সফিকুরের রক্তে পোস্টার ডুবে আছে। পোস্টারের নীল অথবা সবুজ রঙ চেনা যায় না। রক্তের এক রঙ। লাল রঙ। নীল রঙের পোস্টারে অজস্র নক্ষত্রের মতো রক্তবিন্দু লেগে এই মহাকাশকে ব্যঙ্গ করছে। সফিকুরের চোখ বোজা, যেন সে য়ের কোলে ঘুমিয়ে আছে। শিশুর মতো মুখখানি নরম সাদা নীল চোখের মণিকোঠায় একটা মাছি উড়ে উড়ে বসছে।
ফতিমা পাশে স্থির। সবাই মুহূর্তের জন্য কেমন ঠাণ্ডা মেরে গেছে। সে দাঁড়িয়ে সফিকুরের মুখ দেখছিল। মাছিটা কী নির্ভয়ে ওর চোখের ওপর বসে রয়েছে। সে পাশে বসল। চোখ থেকে মাছিটাকে তাড়াল। তারপর কপালে হাত দিয়ে দেখছে—সেই আম-জামপাতার মুকুট ওর মাথায় আছে কিনা! হাত দিতেই সে অনুভব করল, বড় সুন্দর সেই মুকুট, শিশুবয়সের সেই পাতার মকুট। সবাই পাতার মুকুট পরে যেন রাজা-রানী খেলতে যাচ্ছে। সেও সফিকুরের সঙ্গে নদীর চরে। কোন তরমুজ খেতে বুঝি রাজা-রানী খেলতে নেমে যাচ্ছে। সে কপালে হাত দিয়ে বসে থাকল। ফিনকি দিয়ে যে রক্তটা উপচে এসে মুখের চারপাশে পড়েছে—আঁচল দিয়ে সেটা বড় ভালোবাসায় মুছিয়ে দিল। বলতে ইচ্ছা হল, তুমি খেলবে না আমাদের রাজা-রানীর খেলা? সফিকুর বুঝি হাসছে। কেন, আমাকে রাজার মতো লাগছে না? তুমি মাথায় হাত দিলে টের পাবে আমি পাতার মুকুট পরে আছি।
এবার সে সফিকুরের বুকে হাত রাখল। সামনে ভীরু কাপুরুষের মতো পুলিশের দলটাকে আজ ভীষণভাবে উপেক্ষা করতে ভালো লাগছে। বুকে উত্তাপ আছে এখনও। ভালোবাসার উত্তাপ। সে জানে, বেশি সময় বসে থাকতে পারবে না। ওরা ছুটে এসে এক্ষুনি সফিকুরকে ঘিরে ফেলবে। তাড়াতাড়ি সে নীল রঙের পোস্টার মাথার উপর তুলে নিল। ওদের আসবার আগেই এই পোস্টার নিয়ে কোথাও পৌঁছে যেতে হবে। সে সফিকুরকে পিছনে ফেলে এবার হেঁটে যাচ্ছে। ভয় লাগলে সাহস ফিরে পাবার জন্য সে কবিতা বলছে মহাকবির—কখন মরণ আসে কে বা জানে—কালীদহে কখন যে ঝড় ফসলের নাল ভাঙে—ছিঁড়ে ফেলে গাংচিল শালিকের প্রাণ জানি নাকো—তবু যেন মরি আমি এই মাঠ ঘাটের ভিতর…।
এই মাঠ ঘাটের ভিতর তখন আর একজন মানুষ হাঁটছিল। সে ফিরে যাবে তার তরমুজের জমিতে সে কতদিন হল বের হয়েছে দেশ থেকে। তার যেন সহসা মনে পড়ে গেছে, সে এই যে ঘুরে ঘুরে না খেয়ে না দেয়ে কেমন এক ভবঘুরে মানুষের মতো গাছের নিচে বসে থাকছে, কেউ ডেকে খেতে দিলে খাচ্ছে, নয়তো খাচ্ছে না, কেউ বলে না দিলে সে হাঁটছে না—তাকে তরমুজের জমিতে ফিরে যেতে হবে। সে বুঝি বুঝতে পারছে তার মাটির নীচে সামান্য আশ্রয় চাই। সারা দেশ চষে চষে নিজের জন্য সে একখণ্ড জমি পছন্দ করতে পারল না। নদীর চর, তরমুজের খেত মনে হলেই সে বুঝতে পারে ভিতরে তার একটা ভীষণ কষ্ট। অভিমান করে যে সে দেশ ছেড়ে বের হয়ে ছিল, সে-পোড়া দেশে আর সে থাকবে না, শেষ সময়ে মনে হয়েছে সে পৃথিবীর অন্য কোথাও গিয়ে মরে শান্তি পাবে না। সুতরাং অন্নহীন ভূমিহীন ঈশম ফের তার তরমুজের জমিতে গিয়ে বসবে বলে হাঁটছে। গ্রাম মাঠ পার হয়ে সে চলে যাচ্ছে। কারও সঙ্গে কথা বলছে না। সে সোজা হেঁটে যাচ্ছে। না পারলে কোনও গাছতলায় শুয়ে থাকছে। আবার শরীরে সামান্য বল ফিরে এলেই সে হাঁটছে। তার বিরাম নেই বিশ্রাম নেই হাঁটার। তাকে শেষ সময়ে সেখানে যেতেই হবে।
তারপর একদিন সে তরমুজের জমিটার পাশে যখন দাঁড়াল—কে বলবে তখন এই সেই ঈশম। ছেঁড়া তফন। গায়ে জামা নেই। নাকে সর্দি। চোখে পিচুটি। শীর্ণকায়। ক্ষুধায় থরথর করে কাঁপছে। সে দাঁড়াতে পারছে না। কুকুরটা ওর পায়ে পায়ে ঘুরছে। জমির পাশে এসেই মনে হল, এ-জমি তার নয়। জমিটা যে হাজিসাহেবের বেটাদের দিয়ে গেছন ছোটঠাকুর, এতদিন পর কথাটা ফের মনে হতেই ওর ভারি হাসি পেল। ওর মাথায় কী কোথাও গণ্ডগোল হয়েছে! কী করে যে ভুলে গেল, জমিটা তার নয়, অন্যের! অথচ সে দীর্ঘ পথ হেঁটে এসেছে জমিটা নিজের ভেবে। রাতের আঁধারে ফিরে এসেছে বলে কেউ তাকে দেখতে পাচ্ছে না। দেখতে পেলে সবাই কী হাসাহাসি করত! আরে মিঞা তুমি কই আছিলা এদ্দিন! শরীরের দশা এমন ক্যান। য্যান কেউ নাই তোমার? রাইত বিরাতে একা ঘুরলে তোমায় কেউ মনুষ্য কইব না। ঝোপে-জঙ্গলে পালাইয়া থাক। কে কখন কামড়াইব টের পাইবা না।
কী এক ভালোবাসা এই জমির জন্য তার সে নিজেও জানে না, বোঝে না কেন এই ভালোবাসা! সে কেন যে আবার তার জমিতে ফিরে এল! সে ক্ষুধায় কাতর। অন্ধকার বলে কিছু দেখতে পাচ্ছে না। না কী সে বছরের পর বছর ঠিকমতো আহার না পেয়ে অন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ওর বড় ইচ্ছা দেখার এই জমিতে হাজিসাহেবের বেটারা কত বড় তরমুজ ফলিয়েছে। এই জমিতে শুয়ে থাকার ইচ্ছা। সে ভাবল এখানেই আজ রাত কাটিয়ে দেবে। ওর এই মাটি, কত যত্ন করে সে মাটিতে চাষাবাদ করত, কত কষ্ট করে অনাবাদী জমি সে আবাদী জমি করে তুলেছিল। আর সেই দিনের কথা মনে হলে ওর এখনও চোখে জল আসে। সবার কী ঠাট্টা-তামাশা, ঠাকুরের বড় ছেলের মতো ঈশমটাও পাগল! উরাট জমিতে চাষ। কিছু ফলে না জমিতে, কেবল বেনা ঘাস আর বালি। ঈশম বড় যত্নে এবং ভালোবাসায় আবাদ করে কী যে সে করেছিল জমির জন্য মনে করতে পারে না, কেবল মনে হয় সে আলে দাঁড়িয়ে সব তৃষ্ণার্ত মানুষদের তরমুজ কেটে খাইয়েছিল। সে আবার ফিরে এসেছে। তরমুজের পাতার নিচে সে শুয়ে থাকবে। শুয়ে থাকলেই শান্তি। সে শান্তির জন্য পাতা ফাঁক করে উবু হয়ে অন্ধকারে বসল। মাটতে হাত দিল। থাবড়ে-থাবড়ে সে মাটিটার সঙ্গে কথা বলছে। আবার ফিরা আইলাম মা জননী। তর কাছে ফিরা আইলাম। সে মুঠো-মুঠো মাটি তুলে গায়ে মুখে মেখে নিচ্ছে। কাছাকাছি কোথাও কোনও তরমুজ ফলে আছে কি-না হাত দিয়ে খোঁজার চেষ্টা করছে। যেন পেলেই সে একবার পাঁজাকোলে তুলে নেবে। কত ওজন, কত বড়, মা-জননীর সেবা-যত্ন ঠিক না হলে ফসল ফলে না, সে তরমুজ ওজন করে যেন বলতে পারবে হাজিসাহেবের বেটারা কেমন যত্ন-আত্তি নিচ্ছে। কম ওজনের হলে মনে হবে শালারা বেইমান।
সে খুঁজে খুঁজে একটাও তরমুজ পাচ্ছে না। বেশি দূর সে খুঁজতে পারছে না। এখানে এসেই শরীরটা তার ক্রমে কেন জানি স্থবির হয়ে আসছে। হাত পা অসাড়। কেবল কুকুরটা ওর পাশে সেই থেকে আছে। কুকুরটা সেই থেকে কতকাল, এতকাল কুকুর বাঁচে না, তবু কোনও ভালোবাসার আকর্ষণে কেন যে এখনও বেঁচে আছে। কুকুরটাও আর কুকুর নেই, বড়মানুষদের কুকুর কামড়ে সারা শরীরে তার ঘা করে দিয়েছে। সুতরাং কুকুরটার জন্য তার ভারী মায়া। সে কুকুরটাকে ফেলে কোথাও যায়নি, কুকুরটাও তাকে ফেলে কোথাও যাচ্ছে না। এখন একটা তরমুজ পেলে সে কামড়ে একটু রস খেলে আবার কিছুদিন বুঝি বাঁচতে পারত। আবার সে তরমুজের জমিতে বসে নামাজ পড়তে পারত। আর তখনই হাতের কাছে ছোট একটা তরমুজ পেয়ে গেল। তরমুজটা টেনে সে কাছে আনতে পারল না। হামাগুড়ি দিয়ে তরমুজটার কাছে যাচ্ছে। দু’হাতে ভর করে সে যেতে চেষ্টা করছে। তরমুজটাকে সে কাছে আনতে পারছে না। হাত থেকে হড়কে যাচ্ছে। ওর ক্ষুধার্ত মুখ জ্বলছিল। কোনও রকমে সে তরমুজটাকে মুখের কাছে এনে কামড় দেবে, কোনওরকমে একটু তৃষ্ণার জল পান করবে, করলেই গলা ভিজে যাবে, ওর যে নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে সেটা আর থাকবে না। সে কামড়ে দেখল তরমুজটাতে রস নেই। ওর গলা ভিজছে না। সে ক্রমে চোখে ঘোলা দেখছে। মাটির উপর সে দু’হাত বিছিয়ে শুয়ে পড়ল। কুকুরটা বুঝতে পারছে না কেন তার মানুষ এমনভাবে পাতার নিচে লুকিয়ে পড়ছে! মাটিতে হাত-পা ছড়িয়ে উবু হয়ে আছে। নড়ছে না। মানুষটা যে মরে যাচ্ছে কুকুরটা তা বুঝতে পারছে না। রাতে গাছের নিচে ঈশম ঘুমালে সে যেমন পাহারায় থাকে—আজও মানুষটা ঘুম যাচ্ছে বলে শিয়রে জেগে বসে থাকল। সে আর ঈশম, মাথার উপর আকাশ, অজস্র নক্ষত্র এবং অন্ধকার, সোনালী বালির নদী, নদীর জল এবং অর্জুন গাছ মাঠের পাশে। কুকুরটা দুরে শেয়ালেরা উঠে আসছে টের পেল। সে সেই অন্ধকার তরমুজের জমিতে বসে সব লক্ষ রাখছে। সে দু’বার মাটি শুঁকে ঈশমের চারপাশটা একবার ঘুরে এসে শিয়রে বসল। ভয় পেয়েই কুকুর এমন করছে। ভয় পেয়েই কুকুরটা শিয়রে বসে ঘেউঘেউ করে ডাকছে। সারারাত সে সতর্ক থাকছে। শেয়াল-কুকুর ঈশমকে খাবে ভেবেই সে ডাকছে। ঈশম তার মাটির কাছে তরমুজের পাতার নিচে মহানিদ্রায় মগ্ন। আশ্বিনের কুকুর এটা টের পেয়ে আর বসে পর্যন্ত থাকতে পারল না। শত্রুপক্ষ সবদিকে। সে শিয়রে আর বসে থাকছে না, সারাক্ষণ ঘুরছে ঈশমের চারপাশে। কোন দিক থেকে শেয়াল-কুকুরেরা উঠে এসে দাঁত বসাবে কে জানে!
হাজিসাহেবের বেটারা সকালে তরমুজ তুলতে এসে টের পাবে একজন ভিখারি মানুষ তরমুজ পাতার নিচে মরে পড়ে আছে। প্রথমে ঈশমকে ওরা চিনতেই পারবে না। এই ঈশম। ওর কাঠা দুই ভূঁই ছিল বাড়ির পাশে। সেটাও তারা কাঁচা বাঁশের বেড়ায় নিজের করে নিয়েছে। চিনে ফেললেই ভয়। যদি ওটা আবার সে ফিরে চায়। তবু ঈশম এ-পোড়া বাংলাদেশে আবার ফিরে আসতে চায়। আবার জন্ম নিতে চায়। যেন একটা লাঠি দিলে সে এক্ষুনি উঠে দাঁড়াবে। মাথায় পাগড়ি হাতে লণ্ঠন নিয়ে রাতের আঁধারে সে খবর দিতে ছুটবে, ধনমামা, আপনের পোলা হইছে। আমারে কিন্তু একটা তফন দিতে হইব।
অথচ সকালে অঞ্চলের মানুষেরা দেখল নদীর পাড়ে বড় রাস্তায় ঝকঝকে একটা মোটরগাড়ি। এ-গাড়ি দেখলে সবাই টের পা: সামসুদ্দিনসাহেব শহর থেকে এসেছে। সে নদীর পাড়ে গাড়ি রেখে সোজা নিজের গ্রামের দিকে উঠে গেল না। হিন্দু পাড়ার দিকে উঠে যাচ্ছে। খুব কম আসে সামসুদ্দিন। যাদের বয়স বেড়েছে তারা জানে সামু আজকাল সময়ই পায় না। বাড়িতে ওর এখন কেউ নেই। জমিজায়গা দেখার জন্য শুধু একজন লোক আছে। তবু সে বছরে একবার অন্তত আসে। একদিন দু’দিন থাকে, তারপর আবার শহরে চলে যায়। সে কতবারই এসেছে। ভুলেও হিন্দু পাড়ার দিকে উঠে যায়নি। কী যে ভিতরে ছিল কে জানে! সে ওদিকে একেবারেই মাড়াত না। কার কাছে যেন ধরা পড়ে যাবে, কার কাছে বুঝি কী ফেরত দিতে হবে! সে ভয়ে গোপাটে পর্যন্ত নেমে আসত না। কিন্তু আজ এত সকালে সে এদিকে না এসে ওদিকে যাচ্ছে। ওদিকে কিছু নেই। খালি। পাড়াকে-পাড়া খালি। খাঁ-খাঁ করছে সব। সে একা যাচ্ছে না। সঙ্গে দুই যুবতী মেয়ে। ওরা দেখে চিনতেই পারল না, যে মেয়েটা ভোর হলে বটগাছের নিচে ছাগল দিয়ে আসত, যে মেয়ের নাম ফতিমা, নাকে নোলক ছিল, পায়ে মল ছিল, এখন সে মেয়ে কত ডাগর, কী সুন্দর চোখ-মুখ—গাছের পাতার মতো হাওয়ায় কাঁপছে। ফতিমার সুন্দর লতাপাতা আঁকা শাড়িতে প্রায় যেন এই অঞ্চলের দৃশ্য আঁকা রয়েছে। সামু তার মেয়েকে নিয়ে নীরবে হেঁটে হেঁটে চলে যাচ্ছে সেদিকে। যারা ছোটাছুটি করে ওর কাছে গেছে তাদের সঙ্গে কিন্তু সামু কোনও কথা বলছে না। নীরব। বুঝি ওর শৈশবের কথা মনে পড়ে গেছে। পুকুরপাড়ে দাঁড়িয়ে মালতী বুঝি তাকে ডাকছে সামু, যাবি না চুকৈর আনতে। যাবি না নদী সাঁতরে ও-পার। তুই ডুব দিয়া নদীর অতল থাইকা আমার লইগা মাটি তুলবি না? নদীর অতলে মাটি এঁটেল এবং পুতুল তৈরি করতে এমন মাটি আর নেই। সামুর বুঝি মালতীর পুতুলের জন্য মাটি তোলার কথা মনে হচ্ছে।
এখন আর একজন এমন ভাবছে। ফতিমা আনজুর পিছনে। সে বাবার সঙ্গে কতদিন পর দেশে ফিরে এসেছে। গাড়ি থেকে নেমেই সে কেবল শুনতে পাচ্ছে—কেউ তাকে গাছের নিচে দাঁড়িয়ে ডাকছে। সফিকুরের মৃত্যুর পর সে বড় হাহাকারে ভুগছিল। তার কিছু ভালো লাগত না। সে চুপচাপ জানালায় একা দাঁড়িয়ে থাকতে ভালোবাসত। সফিকুর তাকে কী কী বলেছে সব মনে করার চেষ্টা করত। কবে প্রথম দেখা, কিভাবে ফতিমার দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে আবার সহসা নামিয়ে নিয়েছিল সে-সব মনে করার চেষ্টা করত। এসবের ভিতর ফতিমা জানত না সে ক্রমে বিষণ্ণ হয়ে যাচ্ছে। সে জানত না, ওর চোখ বসে যাচ্ছে। সে রোগা হয়ে যাচ্ছে। এবং সে কথা কম বলছে। আম্মা, বা’জান, যখন যে কেউ ওর সঙ্গে কথা বলেছে, সে-কথা শুনতে শুনতে অন্যমনস্ক হয়ে গেছে। বার বার প্রশ্ন করেও জবাব পাওয়া যায়নি। সামু মেয়ের মুখ দেখে ভয় পেয়ে গেছে। সফিকুরের মৃত্যুর পরই মেয়েটা কেমন শোকে পাষাণ হয়ে গেল। সে কিছু করতে পারছে না। মেয়েটা কখনও কাঁদে কি-না চুপি চুপি দেখার চেষ্টা করেছে। ওরা স্বামী-স্ত্রীতে জেগে থেকেছে রাতের পর রাত। ফতিমা রাতে সংগোপনে যদি কাঁদে। দিনের পর দিন মাসের পর মাস ওরা এমন লক্ষ করতে করতে দেখল মেয়েটা সারারাত না ঘুমিয়ে থাকে কিন্তু কাঁদে না। ভিতরে যে অসহ্য কষ্ট চোখ-মুখ দেখলে টের পাওয়া যায়। হাত-পা ছড়িয়ে যদি ফতিমা কখনও মহাশোকে কাঁদতে পারত, সে তবে নিরাময় হতো। সামুর ডাক্তার বন্ধু শেষপর্যন্ত এমন বলেছে। তুমি ওকে কোথাও নিয়ে যাও! পার তো দেশে নিয়ে যাও। সেখানে গেলে ওর শৈশবের কথা মনে হবে। মনে হলে বুঝতে পারবে, কিছুই থেমে থাকে না। এভাবেই মাটি মানুষ এবং নদীর জল বয়ে যায়। শৈশবের ভিতর ফিরে গেলে মানুষের শোক-দুঃখ অনেকাংশে লাঘব হয়।
কথাগুলি সামুর ভালো লেগেছে। সে তার বন্ধুর পরামর্শ মতো এসেছে এই দেশে, বাংলাদেশে। নদীর চরে, তরমুজ খেতে, অজুর্ন গাছের ছায়ায়, হাসান পীরের দরগায় সে যাবে। মেয়েকে বলবে, মা, এই আমার দেশ, তোর দেশ, সবার দেশ। এখানে তুই জন্মেছিস, আমি, মালতী, সোনা, ঈশমচাচা, ফেলু সবাই জন্মেছি। মা, এই দেশ বাংলাদেশ, আমরা সবাই বাংলাদেশের মানুষ। তুই একজনের জন্যে পাষাণ হয়ে থাকবি সে ঠিক না। আয়। বলে সে মেয়ের হাত ধরে, শৈশব বলতে সে যা জেনে এসেছে সেই সোনাবাবু, অর্জুন গাছ এবং লটকন ফল, কচুর পাতায় প্রজাপতি এসবের ভিতর মেয়েকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। আর আশ্চার্য, যেতে যেতে সে সবকিছু ভুলে গেছে। মেয়ের হাত ছেড়ে সেই শ্যাওড়া গাছটার নিচে সে কেন একা একা চলে যাচ্ছে! এখানেই প্রথম মালতী কোটা দিয়ে ওর ইস্তাহারটা নামিয়ে এনেছিল, এখানেই মালতী প্রথম শোকে ভেঙে পড়েছিল। সেই থেকে কেন যে অভিমান করে মালতীর ওপর বার বার সে প্রতিশোধ নিতে চেয়েছে। সে দেখল—সেই ইস্তাহার এখন সে নিজেই ছিঁড়ে ফেলেছে। ছিঁড়ে ফেলে বাতাসে উড়িয়ে দিয়েছে। কাগজের সেই হাজার হাজার টুকরো এখন বাতাসে উড়ছে। কে ক’টা সংগ্রহ করতে পারে—এমন বাজি রেখে মালতী এবং সে ছুটছে। ওরা প্রজাপতির মতো একটা একটা ধরে কোঁচড়ে রাখছে—এমন একটা খেলা চোখের উপর জমে উঠলে ওর মনে হল দূরে গাছের নিচে দাঁড়িয়ে কেউ হাউহাউ করে কাঁদছে। কে এমনভাবে কাঁদতে পারে!
এতক্ষণে ওর খেয়াল হল যে, সে মেয়ের হাত ধরে আসছিল, অথচ মেয়েটা তার পাশে নেই। সামু এখানে এসেই এমন প্রসন্ন সকাল দেখতে পাবে আশা করেনি। জুন মাসের আকাশ। মেঘ-বৃষ্টি থাকার কথা। অথচ একবিন্দু মেঘ নেই আকাশে, মাঠে ছোট ছোট পাটের চারা। ঠাকুরবাড়ির বড় বড় টিনের ঘরগুলি দেখা যাচ্ছে না, আর কেউ কোনওদিন দেখতেও পাবে না। ওর বুকটা ছ্যাৎ করে উঠল। ঠাকুরবাড়ির কোথায় কবে লাঠি খেলা হতো, কবে বাপ আসত সামুর হাত ধরে এবং লাঠি খেলা হলে ঈশমচাচা বাবাকে কিভাবে জড়িয়ে ধরত, মেয়েকে এমন বলতে বলতে আসছিল। যেন এভাবে দেশের কথা শৈশবের কথা ক্রমান্বয়ে বলে যেতে থাকলে মেয়েটা তার আরোগ্যলাভ করবে। ফতিমা তার মহাশোক ভুলে যাবে এবং তখনই সামুর মনে হল, মেয়েটা এইসব শুনতে শুনতে হঠাৎ হাত ছেড়ে বালিকার মতো ছুটেছিল। সে মেয়েটাকে ছুটে যেতে দেখেছে। ছুটে গিয়ে অর্জুন গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে। ফতিমা তার শৈশবের জগতে ফিরে গেছে, সেও তার শৈশবের জগতে ফিরে যাবার জন্য মেয়েকে ফেলে এই গাছের নিচে এসে দাঁড়িয়েছিল। এবং সে কী সব ভাবছিল, ওর পাশে যে গ্রামের কিছু মানুষ দাঁড়িয়ে আছে তা পর্যন্ত সে বুঝতে পারেনি। কারণ, সে যে শিশু বয়সে একবার কী কারণে সেই মেয়েকে মারতে গিয়ে পিঠে দাগ বসিয়ে দিয়েছিল, তারপর আর সে মারেনি। কসম খেয়েছে, সে আর কোনওদিন মেয়ের গায়ে হাত তুলবে না। মেয়েটা তারপর কোনদিন কাঁদেনি। কেবল হেসেছে। ফতিমা হাসলে সে টের পেত ফতিমা হাসছে। কিন্তু কাঁদলে সে টের পায় না–কারণ, ফতিমা এখন বড় হবে গেছে। বড় হলে কান্নার নিয়মকানুন বদলে যায়। সে তবু এর ভিতর টের পেল কেউ কাঁদছে, বাংলাদেশের জন্য কাঁদছে।
সুতরাং সে অস্থির হয়ে উঠল। যেদিক থেকে কান্না ভেসে আসছে সেদিকে সে ছুটল। শৈশবের মতো সে মাঠঘাট পার হয়ে যাচ্ছে। যেখানে দাঁড়িয়ে কেউ বাংলাদেশের জন্য কাঁদতে পারে সেখানে সে চলে যাবেই। সে পৌঁছেই দেখতে পেল–ফতিমা অর্জুন গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে কাঁদছে। আনজু দু’হাতে আগলে রেখেছে ফতিমাকে। বোবার মতো আনজু দেখছে সব বড় বড় অক্ষর গাছে লেখা। সে অক্ষরগুলি পড়ছে। গাছ বড় হয়ে যাওয়ায় অক্ষরগুলি আরও বড় হয়ে গেছে। যেন দেশের মানুষকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখানোর জন্যই অক্ষরগুলি যতদিন যাবে তত বড় হয়ে যাবে। বাংলাদেশের মানুষ বড় বড় হরফে পড়বে, জ্যাঠামশয়, আমরা হিন্দুস্থানে চলিয়া গিয়াছি—ইতি সোনা।
বড় বড় অক্ষর কী গভীর ক্ষত নিয়ে এই মহাবৃক্ষ দাঁড়িয়ে আছে। এ দৃশ্যে সামু নিজে বড্ড বেশি অভিভূত হয়ে গেল। মনে হল তার, এই দেশ বাংলাদেশ। এই দেশে অন্য কোনও জাত নেই, ধর্ম নেই, সে মেয়েকে সান্ত্বনা দেবার কোনও ভাষা পেল না। মেয়ের মাথায় হাত রেখে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল। তখন মাঠ থেকে কিছু লোক ছুটে আসছে। ওরা এসে খবর দিল ঈশম তরমুজের জমিতে মরে পড়ে আছে। কখন সে মরেছে কেউ বলতে পারে না। জমিতে তরমুজ এবার ভাল হয়নি। শুধু পাতা সার। দু’দিনের ওপর হবে জমিতে কেউ তরমুজ তুলতে যায়নি। কেউ জানে না কখন থেকে ঈশম পাতার নিচে মরে পড়ে আছে।
এই জমির এক অংশে ঈশমের জন্য একটু মাটি চেয়ে নিল সামু। এই জমির নিচে ঈশম চুপচাপ শুয়ে থাকবে আবহমান কাল। নানারকম ঘাস জন্মাবে কবরে। ফুল ফুটবে ঘাসে। ঈশমের এই কবর থেকেই বাংলাদেশের ছবিটা স্পষ্ট বোঝা যাবে।
ঈশমের কবরে সামু এবার নতুন একটা ইস্তাহার রেখে দিল। ইস্তাহারটার নাম বাংলাদেশ। তারপর ওকে শুইয়ে দিল। নতুন পাজামা পাঞ্জাবি। সাদা দাড়ি ঈশমের। সে লম্বা হয়ে কবরে শুয়ে আছে। ভূমিহীন অন্নহীন ঈশমের কানে কানে মাটি দেবার আগে বলার ইচ্ছা হল, কিছুই করতে পারিনি এতদিন। স্বাধীনতার মানে বুঝিনি। আপনাকে দেখে মানেটা আমার পরিষ্কার হয়ে গেল। তারপর সে ঈশমের কবরে মাটি দিতে দিতে বলল, যার মাটি পেলে আপনি সবচেয়ে খুশি হতেন চাচা, সে নেই। সে থাকলে তাকে বলতাম, তুমি এসে একটু মাটি দিয়ে যাও বাবু। ওঁর আত্মা বড় শান্তি পাবে। সে বেইমান চাচা। আপনাকে ফেলে সে চলে গেছে। লিখে গেছে জ্যাঠামশাই, আমরা হিন্দুস্থানে চলে গেছি। যেন জ্যাঠামশাই ছাড়া তার বাংলাদেশে কেউ নেই।
তারপর থেকেই মাঝে মাঝে আশ্বিনের কুকুর ঈশমের কবরের পাশে ঘোরাফেরা করলে টের পাওয়া যায় মহাবৃক্ষে সেই ক্ষত আবার মিলিয়ে যেতে শুরু করেছে। অর্জুন গাছটা আরও বড় হচ্ছে। ডালপালা মেলে সজীব হচ্ছে।