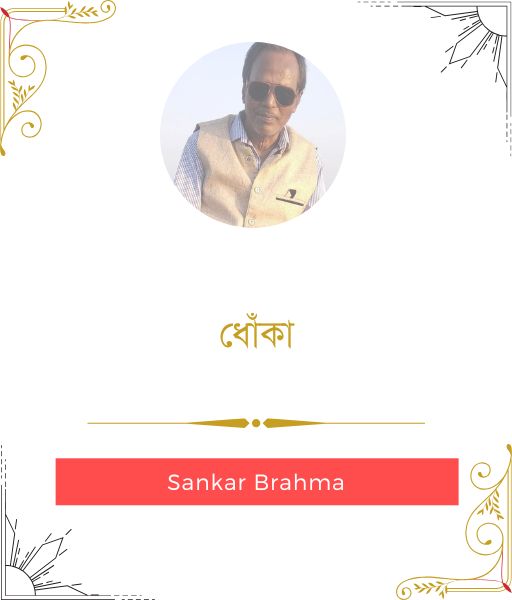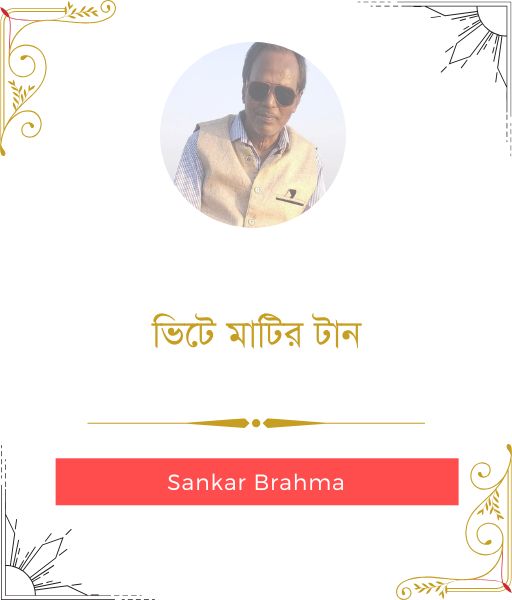নষ্টনীড়
ভূপতির টাকা ছিল যথেষ্ট, কাজ করবার কোনো দরকার ছিল না। উকিল শ্যালক উমাপতির পরামর্শে তিনি একটি ইংরেজী কাগজ বের করেন। কাগজখানা নিয়ে সারাদিন তার ব্যস্ততায় কাটে, বালিকা বধূ চারুলতাকে সময় দিতে পারে না। তাই উমাপতির স্ত্রী মন্দাকিনীকে বাড়িতে এনে রাখে। লেখাপড়ায় চারুলতার ঝোঁক ছিল।
ভূপতির পিসতোত ভাই অমল থার্ড ইয়ারে পড়ে। অমলের কাছে সে পড়া বুঝিয়া নিত বলে, অমলের অনেক আবদার চারুকে সহ্য করতে হত। সে তা করে আনন্দই পেত।
তাদের উঠোনে একটা বিলাতি আমড়া গাছ ছিল। সেখানে একটা মনোরম বাগান তৈরী করার জন্য চারু ও অমলের মধ্য কল্পনা পাখা মেলে। স্বর্গের অমরাবতী তৈরী করে, বাগানে হরিণ থাকবে, ছোটখাট একটি ঝিল থাকবে, যেখানে নীলপদ্ম ফুটবে, হাঁস চড়বে, ঝিলের উপর সাঁকো থাকবে, ঘাটে নৌকা বাঁধা থাকবে। ঘাট হবে সাদা মার্বেলের। এসব পরিকল্পনা অর্থাভাবে শেষে মারা যায়। চারু তখন অমলকে বাগানের বর্ণনা করে কিছু লিখতে বলে। অমল চারুকে ‘আমার খাতা’ নামে একটা প্রবন্ধ পড়ে শুনায়। তারপর থেকে সাহিত্যের মাদক রস তারা উভয়ের গ্রহণ করতে শুরু করে। লেখাই তখন তাদের আলোচনার মুখ্য বিষয় হয়ে ওঠে। চারুর উৎসাহে অমলও লিখতে থাকে নুতন নুতন লেখা। চারুই তার একমাত্র শ্রোতা। চারুও অমলের প্রেরণায় দ্বিধাগ্রস্থভাবে লিখতে শুরু করে। অমলের লেখা কাগজে প্রকাশ হতে শুরু করলে, চারু তখন মনে মনে আহত হয় এই ভেবে যে,অমলে যে লেখা একদিন তার একার সম্পত্তি, তা সকলের হয়ে যাবে? অমল এখন অন্যের আদরের স্বাদ পেয়েছে, ফলে চারুকে বাদ দিলে এখন তার কিছু যাবে আসবে না।
এতদিন অমল এ বাড়িতে আশ্রিত বলে মন্দাকিনীকে তাকে মোটেও গুরুত্ব দিত না। চারুতলা অমলকে গুরুত্ব দেয় দেখে সে মনে মনে সেটাকে ভাল চোখে দেখত না। পাঠক সমাজে অমল মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে দেখে মন্দাকিনী তার প্রতি আকর্ষণ বোধকরে।
এবার মন্দাকিনীকে অমলকে গুরুত্ব দেওয়া শুরু করে,সেটা দেখে তখন চারুলতা সেটা ভাল ভাবে নেয় না। তার মনে অমলকে হারাবার ভয় বাসা বাঁধতে থাকে। সেই ত্রিভূজ প্রেমের দ্বন্দ্ব সারা গল্প জুড়ে নিপুনভাবে বর্ণিত আছে।
এরমধ্যে, উমাপতি বিশ্বাসঘাতকতা করে অর্থ আত্মসাৎ করায়, ভূপতি মর্মাহত হয়ে, মনে বড় আঘাত পায়। তখন সে তার বন্ধু মতিলালের কাছে তার পাওনা টাকা চাইতে গিয়ে, বন্ধুর বেইমানিতে সে টাকাও ফেরৎ পায় না। ফলে ইরেজী কাগজখানা দেনার দায়ে তাকে বন্ধ করে দিতে হয়।
আপদ গেছে ভেবে, তখন ঘরে ফিরে চারুকে সান্নিধ্য দিতে গিয়ে সে টের পায় যে, সে চারুর মনের নাগাল খুঁজে পাচ্ছে না। সেখানে যেন অন্য কারও ছায়া তার মন অধিকার করে আছে। সে ব্যর্থ হয় চারুকে আপন করে ভালবাসতে গিয়ে।
বর্ধমানের উকিল রঘুনাথ বাবুর মেয়ের সঙ্গে অমলের বিয়ে হলে তিনি অমলকে বিলেত পাঠাবেন। এই সংবাদ শুনে অমল রাজি হওয়ায় চারুলতা আশ্চর্য হয়ে যায়। তাকে পরিহাস করে বলে, দেরী হলে বুক ফেটে যাবে তোমার, তুমি টোপর মাথায় দিয়ে এখনই বেরিয়ে পড়। অমল তাতে মোটেও বিচলিত হল না।
অমলের বর্ধমানে বিয়ে হয়ে বিলেত যাবার পর চারুলতা তার কাছ থেকে চিঠি পাওযার আশা করেছিল। হতাশ হয়। অমল বিলেত যাওয়ার পরেও চারুলতার মন আরও বেশি করে সারা সময় জুড়ে অমলের নানা স্মৃতি দগদগে ঘায়ের মতো তার মনে ক্ষত সৃষ্টি করতে থাকে। সে ভূপতিকে না জানিয়ে চাকরকে দিয়ে নিজের সোনার গয়না বেচে অমলকে টেলিগ্রাম করেে। ভূপতি সেটা জানতে পারে।
এবং শেষ সময়ে চারুলতা অমলকে ভালবাসে টের পেয়ে ভূপতি অন্য একটি পত্রিকার সম্পাদক হয়ে চারুকে এখানে রেখে মৈশুরে চলে যাবেন ঠিক করেন। চারু তার সঙ্গে যেতে চাইলেও, প্রথমে তাকে নিয়ে যেতে রাজি হন না। পরে রাজি হলেও, চারু যেতে রাজি হয় না।
এই হল গল্পটির সংক্ষিপ্ত কাহিনি। এই গল্পটি লিখতে রবীন্দ্রনাথ ১৪,৯৫৪টি শব্দ খরচ করেছেন। এখন প্রশ্ন হল এই দীর্ঘ কাহিনিটিকে রবীন্দ্রনাথ উপন্যাস না বলে ছোটগল্প বলেছেন কেন?
সেটা বিচার করে দেখতে গেলে, আমাদের প্রথমেই জানতে হবে ছোটগল্প কা’কে বলে? তারপর জানতে হবে উপন্যাস কাকে বলে?
এবার দেখা যাক ছোটগল্প কা’কে বলে, এই নিয়ে মনীষীরা কে কি বলেছেন?
স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কথা দিয়েই শুরু করা যাক।
“ছোটো প্রাণ, ছোটো ব্যথা,
ছোটো ছোটো দুঃখ কথা
নিতান্ত সহজ সরল,
সহস্র বিস্মৃতিরাশি
প্রত্যহ যেতেছে ভাসি
তারি দু-চারটি অশ্রু জল।
নাহি বর্ণনার ছটা
ঘটনার ঘনঘটা,
নাহি তত্ত্ব নাহি উপদেশ।
অন্তরে অতৃপ্তি রবে
সাঙ্গ করি মনে হবে
শেষ হয়ে হইল না শেষ। “
ছোটগল্প সম্পর্কে বনফুলের মতামত –
” নদীর বুকে অলোর ঝলক
গালের উপর চুর্ণ অলক,
মুচকি হাসি, ত্রস্ত পলক,
হলদে পাখীর টিউ।
বর্ষা ঘন রাত্রি নিবিড়
দেশ বাগিনীর সুমিষ্ট নীড়,
গঙ্গা ফড়িং, বিহঙ্গ নীড়,
টিকিট কেনার কিউ।
জোনাকীদের নেবায় জ্বালায়
রূপসীদের ছলায় কলায়
প্রতিদিনের থামায় চলায়
ছোট গল্প আছে।
পাহাড় কভু, কখনও মেঘ,
কখনও থির, কখনও বেগ,
কান্না কভু, কভু আবেগে
বিদ্যুতেরি নাচে।
এই আছে, এই নেই,
ধরতে গেলে বদলে যে যায়
একটি মুহূর্তেই।
ছোটগল্প বহুরূপী
শিল্পী স্বয়ংবরা,
তাদের কাছেই মাঝে মাঝে
দিয়ে ফেলেন ধরা
গৃহস্থ হন বন্য,
আমরা তখন মহানন্দে
করি ধন্য ধন্য।”
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ছোটগল্পের সংজ্ঞা দিয়ে বলেছেন –
” ছোটগল্প হচ্ছে প্রতীতি জাত একটি সংক্ষিপ্ত গদ্য কাহিনী, যার প্রথম বক্তব্য কোনও ঘটনা বা কোনও পরিবেশ বা কোনও মানসিকতা অবলম্বন করে ঐক্য-সংকটের মধ্য দিয়ে সমগ্রতা লাভ করে”।
রাজশেখর বসু বলেছেন –
” বাংলায় গল্প কথা কাহিনী সমার্থক। মহাভারতের প্রকাণ্ড আখ্যান গল্প, কথামালার ক্ষুদ্র আখ্যানও তাই। ইংরেজীর তরজমা করে আমরা নভেলকে উপন্যাস আর স্টোরিকে গল্প বলি। এককালে রোমান্স অর্থে রমন্যাস চলত, কিন্তু আজকাল শোনা যায় না। সমালোচকরা লিখে থাকেন–অমুক রচনাটি প্রকৃত পক্ষে বড় গল্প, উপন্যাস বলা চলে না। অতএব গল্প বড় হলেই উপন্যাস হয় না। কিন্তু উপন্যাস ছোট হলে কি গল্প হয়?
Concise Oxford Dictionery – Novel is a fictitious prose narrative of sufficient length to fill one or more volumes, portraying characters & actions representative of real life in continuous plot.
ওই অভিধানে story-র অর্থ–tale of any length told or printed in prose or verse of actual or fictitious events, legends, myth, anecdote, novel, romance.
উক্ত সংজ্ঞার্থ অনুসারে রূপকথা পুরাণকথা কিংবদন্তী নকশা বা স্কেচ, নভেল প্রভৃতি ছোট বড় সব রকম আখ্যান স্টোরির অন্তর্গত।
আর উপন্যাস?
উপন্যাসের ভিত্তি একটি দীর্ঘ কাহিনী। যেখানে মানব-মানবীর তথা ব্যক্তির সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গ, ঘৃণা-ভালোবাসা ইত্যাদি ঘটনা প্রাধান্য লাভ করে। উপন্যাসের প্লট বা আখ্যান হয় সুপরিকল্পিত ও সুবিন্যস্ত। প্লটের মধ্যে ঘটনা ও চরিত্রের ক্রিয়াকাণ্ডকে এমনভাবে বিন্যস্ত করা হয় যাতে তা বাস্তব জীবনকে প্রতিফলিত করে এবং কাহিনীকে আকর্ষণীয়, আনন্দদায়ক ও বাস্তবোচিত করে তোলে।
উপন্যাস বিশ্লেষকগণ একটি সার্থক উপন্যাসের গঠন কৌশল নিয়ে ছয়টি রীতির কথা বলেছেন।
১). প্লট বা আখ্যান
উপন্যাসের ভিত্তি একটি দীর্ঘ কাহিনী। যেখানে মানব-মানবীর তথা ব্যক্তির সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গ, ঘৃণা-ভালোবাসা ইত্যাদি ঘটনা প্রাধান্য লাভ করে। উপন্যাসের প্লট বা আখ্যান হয় সুপরিকল্পিত ও সুবিন্যস্ত। প্লটের মধ্যে ঘটনা ও চরিত্রের ক্রিয়াকাণ্ডকে এমনভাবে বিন্যস্ত করা হয় যাতে তা বাস্তব জীবনকে প্রতিফলিত করে এবং কাহিনিকে আকর্ষণীয়, আনন্দদায়ক ও বাস্তবোচিত করে তোলে।
২). চরিত্র
ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সম্পর্কের মাধ্যমে সৃষ্টি হয় সমাজ-সম্পর্ক। এই সম্পর্কজাত বাস্তব ঘটনাবলি নিয়েই উপন্যাসের কাহিনী নির্মিত হয়। আর, ব্যক্তির আচরণ, ভাবনা এবং ক্রিয়াকাণ্ডই হয়ে ওঠে উপন্যাসের প্রধান বর্ণনীয় বিষয়। উপন্যাসের এই ব্যক্তিই চরিত্র বা Character. অনেকে মনে করেন, উপন্যাসে ঘটনাই মুখ্য, চরিত্র সৃষ্টি গৌণ। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে, ঘটনা ও চরিত্র পরস্পর নিরপেক্ষ নয়, একটি অন্যটির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। মহৎ ঔপন্যাসিক এমনভাবে চরিত্র সৃষ্টি করেন যে, তারা হয়ে ওঠে পাঠকের চেনা জগতের বাসিন্দা বা অতি পরিচিতজন। উপন্যাসের চরিত্র হিসেবে একজন লেখকের অন্বিষ্ট হয় দ্বন্দ্বময় মানুষ। ভালো-মন্দ, শুভ-অশুভ, সুনীতি-দুর্নীতি প্রভৃতির দ্বন্দ্বাত্মক বিন্যাসেই একজন মানুষ সমগ্রতা অর্জন করে এবং এ ধরনের মানুষই চরিত্র হিসেবে সার্থক বলে বিবেচিত হয়।
৩). সংলাপ
বিখ্যাত ইংরেজ ঔপন্যাসিক E. M. Forster – এর মতে, কমপক্ষে পঞ্চাশ হাজার শব্দ দিয়ে উপন্যাস রচিত হওয়া উচিত। উপন্যাস সাহিত্যের এমন একটি মাধ্যম যেখানে বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়ার অবকাশ থাকে। এখানে লেখক প্রাণখুলে তার মতামত লিপিবদ্ধ করতে পারেন বা একেকটি চরিত্রকে প্রস্ফুটিত করতে পারেন সকল ধরনের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে। উপন্যাসকে এক সুবিশাল ক্যানভাস হিসেবে ধরা যায়, লেখক তার পরিকল্পনা মাফিক একেকটি অধ্যায়কে জায়গা করে দেন সেখানে।
স্থান-কালের যথার্থ উল্লেখ, বাস্তবতার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা, মানুষের হৃদয়ের গভীর তলদেশ স্পর্শ করার ক্ষমতা—ইত্যাদি দরকার একটি সার্থক উপন্যাসের জন্য।
উপন্যাসের ঘটনা প্রাণ পায় চরিত্রগুলোর পারস্পরিক সংলাপে। যে কারণে ঔপন্যাসিক সচেষ্ট থাকেন স্থান-কাল অনুযায়ী চরিত্রের মুখে ভাষা দিতে। অনেক সময় বর্ণনার চেয়ে চরিত্রের নিজের মুখের একটি সংলাপ তার চরিত্র উপলব্ধির জন্য বহুল পরিমাণে শক্তিশালী ও অব্যর্থ হয়। সংলাপের দ্বারা ঘটনাস্রোত উপস্থাপন করে লেখক নির্লিপ্ত থাকতে পারেন এবং পাঠকের বিচার-বুদ্ধির প্রকাশ ঘটাতে পারেন। সংলাপ চরিত্রের বৈচিত্র্যময় মনস্তত্ত্বকে প্রকাশ করে এবং উপন্যাসের বাস্তবতাকে নিশ্চিত করে তোলে।
৪). পরিবেশ বর্ণনা
উপন্যাসের কাহিনীকে হতে হয় বাস্তব ও বিশ্বাসযোগ্য। ঔপন্যাসিক উপন্যাসের দেশকালগত সত্যকে পরিস্ফুটিত করার অভিপ্রায়ে পরিবেশকে নির্মাণ করেন। পরিবেশ বর্ণনার মাধ্যমে চরিত্রের জীবনযাত্রার ছবিও কাহিনীতে ফুটিয়ে তোলা হয়। এই পরিবেশ মানে কেবল প্রাকৃতিক দৃশ্য নয়; স্থান কালের স্বাভাবিকতা, সামাজিকতা, ঔচিত্য ও ব্যক্তি মানুষের সামগ্রিক জীবনের পরিবেশ। দেশ-কাল ও সমাজের রীতি-নীতি, আচার-আচরণ, প্রথা ইত্যাদি নিয়ে গড়ে ওঠে উপন্যাসের প্রাণময় পরিবেশ।
৫). শৈলী বা স্টাইল
শৈলী বা স্টাইল হচ্ছে উপন্যাসের ভাষাগত অবয়ব সংস্থানের ভিত্তি। লেখকের জীবনদৃষ্টি ও জীবনসৃষ্টির সঙ্গে ভাষা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। উপন্যাসের বর্ণনা, পরিচর্যা, পটভূমিকা উপস্থাপন ও চরিত্রের স্বরূপ নির্ণয়ে অনিবার্য ভাষাশৈলীর প্রয়োগই যে কোনও ঔপন্যাসিকের কাম্য। উপজীব্য বিষয় ও ভাষার সামঞ্জস্য রক্ষার মাধ্যমেই উপন্যাস হয়ে ওঠে সমগ্র, যথার্থ ও সার্থক আবেদনবাহী, উপন্যাসের লিখনশৈলী বা স্টাইল নিঃসন্দেহে যে কোনো লেখকের শক্তি, স্বাতন্ত্র্য ও বিশিষ্টতার পরিচায়ক। তাই চিন্তার মননশীলতার পরিচয় ও পাওয়া যায় বটে। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর হাতে বাংলাদেশের উপন্যাসের যে শৈল্পিক সূচনা হয়েছিল, আখতারুজ্জামান ইলিয়াসে এসে তা পূর্ণতা লাভ করে। তবে বাংলাদেশের উপন্যাসের এ গতিপ্রবাহ থেমে যায়নি। একবিংশ শতকে সম্পূর্ণ নতুন ধারার উপন্যাসের সূত্রপাত যে ঘটবে তার পূর্বাভাস পরিলক্ষিত হচ্ছে।
৬). লেখকের সামগ্রিক জীবন-দর্শন
মানব জীবন-সংক্রান্ত যে সত্যের উদ্ঘাটন উপন্যাসের মধ্য দিয়ে পরিষ্ফূট হয় তাই লেখকের জীবনদর্শন। আমরা একটি উপন্যাসের মধ্যে একই সঙ্গে জীবনের চিত্র ও জীবনের দর্শন এই দুইকেই খুঁজি। এর ফলে সার্থক উপন্যাস পাঠ করলে পাঠক মানব জীবন-সংক্রান্ত কোনও সত্যকে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারেন। উপন্যাসে জীবনদর্শনের অনিবার্যতা তাই স্বীকৃত।
উপন্যাসের মানদন্ডে ‘নষ্টনীড়’ পড়ে না। তাই রবীন্দ্রনাথ ‘নষ্টনীড়’-কে উপন্যাস না বলে, ছোটগল্প বলেছেন।