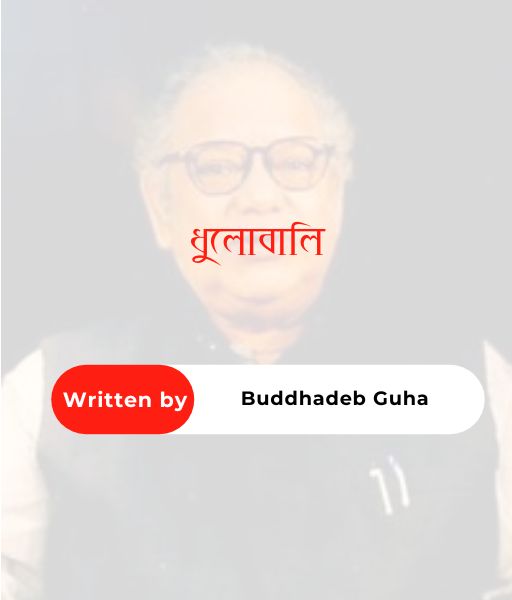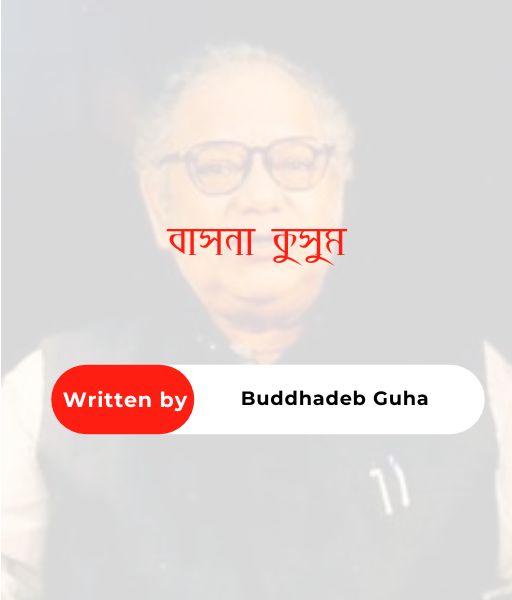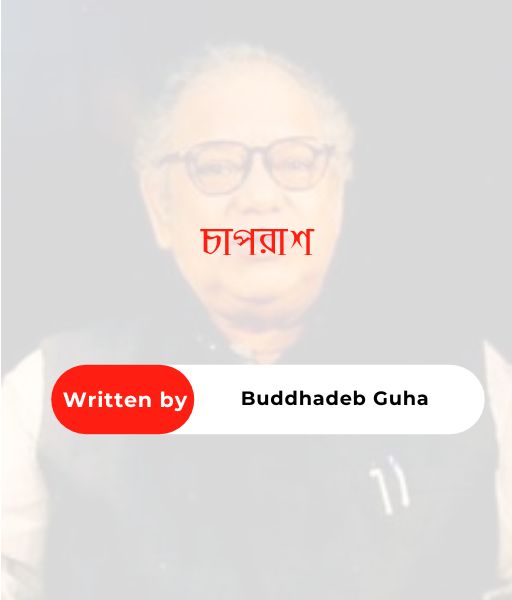বরিশাল থেকে ফিরে
১১.
বরিশাল থেকে ফিরে আসার দু-তিন বছর পরই বাবা সরকারি চাকরিতে ইস্তফা দেবেন বলে মনস্থির করলেন। সেদিনকার কথা পরিষ্কার মনে আছে আমার। তখনও বেশ ছোটোই ছিলাম।
বাবা একদিন এসে বললেন তোমাকে যে সম্মানের সঙ্গে আর চাকরি করা সম্ভব নয়। এবারে চাকরিটা ছেড়েই দিতে হবে।
তোমার দু-চোখে আতঙ্ক ফুটে উঠল। মুহূর্তের জন্যে সে আতঙ্ক দু-চোখের মণিতে দপ দপ করে জ্বলে উঠেই আবার প্রগাঢ় নিশ্চিন্তিতে স্থির হয়ে গেল।
কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তুমি বললে যে, আমি কি অতসব বুঝি? তুমি যা ভালো মনে করবে তাই-ই করবে।
সে-রাতে বাবার মাথার চুল তিন-চতুর্থাংশ পেকে গেল। চিন্তা-ভাবনায় মানুষের চুল পাকে; তা আগে শুনেছিলাম। কিন্তু চোখের সামনে একরাত্তিরে যে মানুষের মাথার চুল এভাবে পাকতে পারে, তা বাবাকে না দেখলে জানতাম না।
স্বাধীনতার পর পর সরকারি চাকরিতে তখন সবে উন্নতির ক্ষেত্রে একে অন্যকে ডিঙিয়ে যাওয়ার মহরত হয়েছে। তার আগে ব্রিটিশ আমলে সুপারসেশন শব্দটি তেমন পরিচিত ছিল না। দেশ স্বাধীন হবার পর পর বাবাকে দেখেছি বহু দেরি করে বাড়ি ফিরতে অফিস থেকে।
মা জিজ্ঞেস করলে বলতেন, এখন আমাদের নিজেদের সরকার, নিজেদের দেশ, এখন কি আর সময়ের হিসেব করে কাজ করলে চলে? অনেক বেশি কাজ করতে হবে, অনেক বেশি টাকা আদায় করে দিতে হবে সরকারকে। কিন্তু বাবার এই আন্তরিকতা সত্ত্বেও, অত্যন্ত ভালো সি সি আর থাকা সত্ত্বেও কোনো দুর্বোধ্য কারণে তাঁর পর পর দু-বার উন্নতি আটকে গেল। এবং সে কারণেই বাবা চাকরি ছেড়ে দেবেন বলে রাতারাতি সিদ্ধান্ত নিলেন।
তখন বাবার ওপরওয়ালা ছিলেন মুখার্জিজেই। ছোটোখাটো মানুষটি। সব সময় ভারি রসিক, আমুদে এবং প্রাণচঞ্চল। তাঁর প্রত্যেকটা কথার নিদেনপক্ষে তিনটে করে মানে হত। এরকম তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ আমি আমার জীবনে খুব কম দেখেছি।
মুখার্জিজেঠু বাবা এবং তোমাকে বিশেষ স্নেহ করতেন। উনি নিজে পরদিন বাড়িতে দৌড়ে এলেন। এসে তোমাকে অনেক করে বোঝালেন, মিসেস রায়, স্বামীকে বুঝিয়ে বলুন এরকম পাগলামি না করতে। দু-বার অন্যায় হয়েছে বলে কি চিরদিনই অন্যায় হবে? এবার নিশ্চয়ই প্রমোশন হবে। এইরকম হঠকারী সিদ্ধান্ত ওকে নিতে মানা করুন।
তখন কাকারা কেউ কিছুই করেন না বলতে গেলে; মানে অর্থকরী করা। রংপুরের বিষয় সম্পত্তি সমস্তই জলে যাবার উপক্রম দেশভাগের পর। দেশভাগ সবে হয়েছে। আমিই বাবার বড়োছেলে, তখন অত্যন্ত ছোটো। ক্লাস সিক্সে পড়ি। আগেই বলেছি।
সে যাই হোক, বাবা সিদ্ধান্ত যখন নিলেন, তখন সেইমতোই পদত্যাগপত্র পেশ করে দিলেন। কলকাতায় তখন এক নামকরা উকিল ছিলেন। মুসলমান ভদ্রলোক। তাঁর প্রচন্ড পসার, এবং তীক্ষ্ণধী মানুষ হিসেবে তাঁকে সকলেই সম্মান করতেন।
তিনি বাবার এই স্বাধীনচেতা এবং সাহসী মনোভাব দেখে বললেন, কোনো ভয় নেই রায়। তুমি আমার অফিসের বারান্দায় টেবিলচেয়ার নিয়ে বসে পড়ো। ভালো করে যদি খাটো, তাহলে একদিন তুমি চাকরিতে যা রোজগার করতে, তার বহুগুণ বেশি রোজগার করবে নিঃসন্দেহে। তবে নিজের স্বাধীন পেশায় সততা ও পরিশ্রম সবচেয়ে বড়ো কথা।
বাবার স্বাধীন পেশার জীবনের প্রথম দিন সন্ধ্যাবেলা বাবা বাড়ি ফিরলেন, সেদিন আমার জ্বর হয়েছিল। আমি তোমার ঘরেই শুয়েছিলাম। বাবার পাশের ঘরে তোমার ঘর। বাবা এসে তোমাকে একটা একশো টাকার নোট দিলেন। দিয়ে বললেন, এই আমার স্বাধীন জীবনের প্রথম রোজগার, এই নোটটিকে সিঁদুর মাখিয়ে আলমারিতে তুলে রাখো।
তুমি তখনকার দিনের সেই বড়ো একশো টাকার নোটটিকে সিঁদুর মাখিয়ে আলমারিতে তুলে রাখলে।
তারপর বাবার কাছে বলে বসলে, একটা কথা বলব?
বাবা বললেন, বল।
তুমি বললে, তুমি চাকরি ছেড়ে দিয়ে ভালো করলে কি মন্দ করলে জানি না। কিন্তু যাই-ই করো না কেন, আমি তোমার মতেই চিরদিন মত দিয়ে এসেছি।
তারপর একটু চুপ করে থেকে বললে, একটা কথা ভেবে আমার ভালো লাগছে, সে কথাটা এই, তুমি এতদিন যেহেতু সরকারি চাকরি করতে, কোনোদিন বাড়ি ফেরার সময় হাতে করে গঙ্গার ধার থেকে কিনে একটা ইলিশ মাছ নিয়ে এলে প্রতিবেশীরা আর বলতে পারবেন না যে, সরকারি চাকরি করে তো। সরকারি চাকরিতে কত কী উপরি রোজগার থাকে। বড়ো বড়ো মাছ তো ওরা খাবেই! এই অসম্মানের কথাটা যে আর কখনো শুনতে হবে না, এটা ভেবেই আমার ভারি আনন্দ হচ্ছে।
বাবার নতুন স্বাধীন পেশাতে বাবা দেখতে দেখতে অচিরে অত্যন্ত উন্নতি করলেন। কী যে অমানুষিক পরিশ্রম করলেন তখন। বড়োছেলে হিসেবে বয়েসে ছোটো হলেও আমার পরিষ্কার মনে আছে। রাতে বাবা অনেকদিন বাড়ি ফিরতে পারতেন না। অফিসের টেবিলেই শুয়ে থাকতেন। তখন বাবার ছোট্ট অফিসে দু-তিনজন কর্মচারী ছিলেন। তাঁরাও অমানুষিক পরিশ্রম করতেন বাবারই মতো।
যখন তাঁদের ছুটি হত, তখন শেষ ট্রাম, শেষ বাস, সব উঠে গেছে শহর থেকে। অত রাতে, বর্ষা-বাদলে, কী প্রচন্ড শীতের রাতেও চার-পাঁচ মাইল দূরে হেঁটে হেঁটে তাঁদের নিজের নিজের বাড়িতে যেতেন। বাবার সেই নতুন অফিসের যে অ্যাসিস্ট্যান্ট এবং কর্মচারীরা ছিলেন, তাঁদের কাউকে কখনোই দেখে মনে হয়নি যে, তাঁরা পয়সার বিনিময়ে কাজ করতেন।
তাঁরা সকলেই বউদি বলতে অজ্ঞান ছিলেন। তোমার শান্ত, স্নিগ্ধ, সুন্দর হাসি, তোমার আন্তরিক ব্যবহার, স্নেহ মমতা যে তাঁদের প্রত্যেকের ওপরে কত গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল, তা বলার নয়। আজকাল সেসব লোক আর দেখা যায় না। নির্মলকাকু, নরেনকাকু, শৈলেনকাকু ইত্যাদি বাবার তৎকালীন সহকারীরা যেভাবে এবং যে আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করতেন, সে আন্তরিকতা ও আপনারবোধ এখনকার দিনে অত্যন্ত বিরল! তাঁরা কখনোই একথা মনে করতেন না যে, টাকা রোজগারের জন্যে তাঁরা কাজ করতে এসেছেন। একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবেন, নাম হবে, যশ হবে, এটাই ছিল তখন সবচেয়ে বড়ো কন্সিডারেশন। কার নিজের কতটা লাভ হবে এবং আদৌ হবে কি না একথা তখনকার দিনে কম মানুষই হয়তো ভাবতেন।
আমাদের বাড়িতে তখন কাজ করত উষা বলে একটি ছেলে। সে রান্না করত না, তবে চা জলখাবার দেওয়া, অন্যান্য ফরমাশ-খাটা এসব কাজ তার ছিল। আমাদের বাড়িতে কাজ করতে আসার আগে সে এক রেস্টুরেন্টে কাজ করত। অদ্ভুত কায়দায় দু-হাতে আট-দশ কাপ চা একের পর এক সাজিয়ে নিয়ে তিরবেগে সে দৌড়োদৌড়ি করত বাড়িময়। তুমি তখন বলতে, ফেলে দিয়ে আসবাব পত্র তো নষ্ট করবিই, উপরন্তু ছ্যাঁকা খাওয়াবি কত লোককে।
তার যতরকম কৃতিত্ব ছিল রেষ্টুরেন্টের চাকরিতে শেখা; উষা আমাদের কাছে সে-সমস্ত দেখিয়ে বাহাদুরি নিত।
বাবার নতুন অফিসে একজন বেয়ারার দরকার, যে চা-জলখাবার বানাতে পারে। উষাকে একদিন তুমি সে-কথা বললে।
উষা বলল, মা, আমার দাদা তো বসেই আছে কিছুই করে না, পাকিস্তান থেকে চলে এসেছে, এখানে প্রায় না-খেয়েই রয়েছে। আপনি ওকে বাবুর অফিসে ঢুকিয়ে দিন।
পরের দিন উষার দাদা বিশু, মার কাছে ইন্টারভিউ দিতে এল। অতি ছোটোখাটো ধবধবে ফর্সা, সাদা ধুতি সাদা শার্ট পরনে, মাথা-ভরতি কোঁকড়া চুল, অত্যন্ত লাজুক মানুষ। কে বলবে যে উষার দাদা সে, একটু মেয়েলি মেয়েলি ও; এসে মার সামনে দাঁড়াল।
তুমি বললে, বা: বেশ তো চেহারা! লেগে যাও তুমি কাল থেকেই বাবুর অফিসে।
রবিবার ছিল বলে বাবা বাড়িতেই ছিলেন। বাবা তাকে ডাকলেন।
বললেন, তুই এর আগে কী করেছিস? কী কাজ করতিস?
বিশু বলল, ইসমাগলিং।
বাবা বললেন, কী?
বিশু আবারও বলল, ইসমাগলিং।
তুমি বললে, কী? তার মানে?
বিশু বলল, চাল আর চিনি লোকাল ট্রেনে এনে কলকাতা শহরে বিক্রি করি। স্মাগলিং কথাটা তার আগে কলকাতায় অত চালু ছিল ন। দেশবিভাগের পর যখন কর্ডনিং প্রথা চালু হল এবং প্রচুর নিরুপায় বাস্তুহারারা এসে পড়ল এদেশে তখন থেকে বাঙালির রক্তে একটি দুর্ভাগ্যজনক শব্দ ধমনি বেয়ে বইতে লাগল। একটা উদার সংস্কৃতিসম্পন্ন হাসিখুশি সরল সোজা জাতকে রাজনৈতিক ঘটনাচক্রে এক অতিনীচ অথচ উপায়হীন পথে নেমে কেবলমাত্র বেঁচে থাকবার জন্যে অনেক কিছুই করা আরম্ভ করতে হল। অনেক কিছু অভাবনীয় ক্রিয়াকান্ডর সেই শুরু।
পুরোনো কথা মনে এলে অনেক কথাই মনে হয়। তোমার স্মৃতিচারণের মধ্যে এসব কথা হয়তো অপ্রাসঙ্গিক। তবু তোমার কথা মনে পড়তে পেছন ফিরে তাকালে অনেক অনেক কথা মনে আসে।
নরেনকাকু বাবার অফিসে কাজ করতেন। তিনি দেশবিভাগের পর বরিশাল থেকে এসেছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি ছিল না তাঁর, কিন্তু জীবনে খড়কুটোর মতো ভেসে-যাওয়া মানুষটির প্রধান সম্বল ছিল কাজ শেখার ইচ্ছা। যে পায়ের তলা থেকে সব মাটি ধুয়ে গেছে, সেই পায়ের তলায় নতুন মাটি পাওয়ার ইচ্ছা। এইসব, এইসবই ছিল তাঁর মূলধন।
তখন আমরা বরিশালেই কাঠপট্টিতে একটা দোতলা বাড়িতে ভাড়া থাকতাম। সেই বাড়ির উলটোদিকে ছিল একটি মনোহারী দোকান। সেই দোকান সকালে-বিকেলে এসে খুলতেন নরেনকাকু। সাইকেল-রিকশা করে এসে কালো মিষ্টি চেহারার এক ভদ্রলোক সাদা ধুতি ও হাত গোটানো সাদা শার্ট পর এসে নামতেন একগোছা চাবি নিয়ে। তারপর সে চাবি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দোকানের দরজার বিভিন্ন তালা খুলতেন। তালা খুলে দরজা ভাঁজ করে বাইরের দিকে খুলে দিয়ে ভেতরে ঢুকে ঝুল-ঝাড়া ঝাড়ন দিয়ে দোকান পরিষ্কার করতেন। বাইরে একটু জলের ছিটে দিতেন ভেতরে ধূপকাঠি জ্বালাতেন।
মনোহারী দোকান ছিল। আমিও মাঝে মাঝে সে-দোকানে যেতাম সওদা করতে। ছোট্ট মফসসল শহরে, সরকারি অফিসারের ছেলে-মেয়েদেরও সেই সময় বিশেষ খাতির হত। একটা কাঠের টুল উনি আমাকে এগিয়ে দিতেন বসবার জন্যে। টেবিলফ্যানটা মাঝে মাঝে ঘুরিয়ে দিতেন আমার দিকে, তারপর সাবান কী অন্য কিছু যা কেনার জন্য আমি যেতাম, সেই সামগ্রী এগিয়ে দিতেন আমায়।
নরেনকাকু একটু একটু টাইপ জানতেন। সেই টাইপের জ্ঞানটুকু সম্বল করেই উনি যখন বরিশাল ছেড়ে কলকাতা এলেন, তখন তাঁর দোকানের যিনি মালিক ছিলেন, বাবার এক বিশেষ পরিচিত ভদ্রলোক, তাঁরই অনুরোধে বাবা নরেনকাকুকে অফিসে নিলেন।
সামান্য প্রতিষ্ঠানিক বিদ্যা সম্বল করে একজন মানুষ তাঁর পরিশ্রমের গুণে এবং তাঁর বড়ো হওয়ার জেদে যে কতখানি পথ এগিয়ে আসতে পারেন, নরেনকাকু তার এক জাজ্বল্যমান উদাহরণ। নরেনকাকু, নির্মলকাকুরা সকলেই যুক্ত ছিলেন বাবার কাজে কিন্তু তুমি আড়াল থেকে তাঁদের প্রত্যেকের ওপরে এক বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিলে তোমার অননুকরণীয় ব্যবহারে।
.
১২.
তুমি আমার জন্য বরাবরই গর্বিত ছিলে। তোমার সেই গর্ব আমার ওপর এক গুরুভার দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছিল তোমার গর্বের যোগ্য হওয়ার জন্যে। আমার সবকিছু নিয়েই তুমি গর্ব করতে। হয়তো করতে তোমার অন্য ছেলে-মেয়ের ভালোটুকুও নিয়ে। কিন্তু যেহেতু আমিই প্রথম সন্তান, তোমার স্নেহ বিশেষভাবে ছিল আমার ওপর।
আমি যখন বড় হয়েছি, যখন কোনো বিয়েবাড়িতে নেমন্তন্নে যেতাম, যাবার আগে ধুতি পাঞ্জাবি পরে তোমাকে একবার সাজ না-দেখিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। তা না হলে তুমি আমাকে ডেকে পাঠাতে। বলতে, বা:, তোকে কী সুন্দর দেখাচ্ছে!
সুন্দর হয়তো অনেককেই দেখায়। কিন্তু সে সৌন্দর্য, সে শারীরিক বা মানসিক সৌন্দর্যই হোক না কেন অ্যাপ্রিশিয়েট করার লোক সংসারে নিজের মায়ের মতো অন্য কেউই থাকে না। তুমি আমার সবকিছু নিয়ে যেমন প্রীত এবং গর্বিত ছিলে তেমন এ জীবনে আর কেউই হবে না।
তোমার কথা যখন ভাবি, তখন একটা কথা সবচেয়ে বেশি মনে হয়, সেটা হচ্ছে এই যে, আর্থিক অবস্থার তারতম্য তোমার ভেতরের মানুষটিকে এতটুকুও বদলাতে পারেনি। যে-তুমি তোমার বিয়ের পরে বেশ কয়েক বছর আর্থিক অনটনের মধ্যে ছিলে, সেই তুমিই অর্থের অশেষ প্রাচুর্য দেখে গেছ তোমারই জীবনে। কিন্তু যে দরদি, সমব্যথী, সরল এবং পরের দুঃখে কাতর মানুষটিকে আমি চিনতাম, সেই মানুষটিকে এতটুকুও পরিবর্তিত দেখিনি অসীম প্রাচুর্যের মধ্যেও।
দারিদ্র্য বেশির ভাগ মানুষকেই বড়ো হীনম্মন্য করে তোলে। এবং সেই দারিদ্র্য যখন নিজের জীবনেই প্রাচুর্যে পর্যবসিত হয়, তখন বেশির ভাগ মানুষই উচ্চম্মন্যতায় ভোগে। পুরোনো জীবনের সব কথা ভুলে যায়। অনেকে পুরোনো জীবনকে ঘৃণাও করতে শেখে, সে জীবনকে অস্বীকার করে বিস্মৃতির অন্ধকার গভীরে ঠেলে দেয়। সংসারে এর ব্যতিক্রম বড়ো একটা দেখি না।
কিন্তু তুমি ব্যতিক্রম ছিলে।
ছেলেবেলাতেও যেমন দেখেছি, বড়োবেলাতেও তেমন তোমার মনের অনেক দিক আমি নীরবে এবং নিঃশব্দে প্রত্যক্ষ করেছি।
আমাদের এক দূরসম্পর্কের আত্মীয়া একদিন দুপুরে আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন, যখন আমাদের অবস্থা যথেষ্ট ভালো। সেই আত্মীয়া ভারি চমৎকার মানুষ ছিলেন। অতিসুন্দরী, বিদুষী এবং গুণবতী। কিন্তু এদেশের বিবাহিতা মেয়েদের রূপ-গুণ কিছুই, একটা সময় পর্যন্ত স্বীকৃতি পেত না, যদি-না তাদের স্বামীরা উপযুক্ত হত। হয়তো এখনও স্বীকৃতি পায় না।
এমন যে মহিলা তাঁর স্বামী তাঁর উপযুক্ত ছিলেন না। যোগ্যতা যে ছিল না তাঁর, তা নয়। অত্যন্ত কৃতবিদ্যমানুষ ছিলেন তিনি। কিন্তু রেসের মাঠে তিনি তাঁর সমস্ত যোগ্যতা কবরস্থ করেছিলেন। তিনি একদিন শীতের দুপুরে এলেন। তুমি এসে বিনুকে বললে, তোর আলমারিতে ক-টা শাড়ি-শায়া আছে?
বিনু বলল, কেন মা?
তুমি বললে, ও এসেছে শুধু শাড়ি পরে। ওর একটা শায়া পর্যন্ত নেই।
বিনু সেদিন আলমারি খুলে তোমাকে বলেছিল, যতগুলো শাড়ি দরকার মা তুমি নিয়ে যাও।
তুমি নিজের শাড়িও দিতে পারতে। কিন্তু ছেলে-মেয়েরা বড়ো হয়ে যাবার পর রঙিন শাড়ি তুমি একেবারেই পরতে না, সে কারণেই তুমি মেয়ের শরণাপন্ন হয়েছিলে শাড়ির ব্যাপারে।
তুমি যে কত লোককে সাহায্য করতে, কত লোক যে তোমার মাসিক মাসোহারায় অভ্যস্ত ছিল, তা শুধু জানা গেল তোমার মৃত্যুর পরে। তুমি সবসময় বলতে, আহা! ওর কত কষ্ট! সে যেই হোক না কেন! তার কষ্ট লাঘব করার জন্য তুমি করতে না, বা করতে পারতে না এমন কিছুই ছিল না। আমার হাত দিয়ে তুমি গোপনে কত লোককে কত কিছু দিয়েছ, কত আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি আমি সাইকেল চালিয়ে টাকা পৌঁছিয়ে দিয়ে এসেছি ছেলেবেলা, সেকথা এক তুমি জানতে আর আমি জানতাম। আজ অবধি বাবাও সেকথা জানেন না। কিন্তু যাদের কষ্টকে তুমি নিজের বুকের কষ্ট করেছিলে, তাদের মধ্যে অনেকেই তোমাকে কষ্ট দিতে একটুও দ্বিধা করেননি। সেসব চরিত্র বোধ হয় এইরকমই হয়।
যে করে, তাকেই বোধ হয় মানুষ পেয়ে বসে। যে ভালো, যে নরম, তাকে মানুষ শক্ত এবং খারাপ হতে বাধ্য করে ধীরে ধীরে তাদের হৃদয়হীন অত্যাচারে; তাদের বিবেকহীনতায়।
এ-পৃথিবী বড়ো অকৃতজ্ঞ পৃথিবী। তোমার মাধ্যমে, তোমার ক্রিয়াকর্মের মাধ্যমে এবং তার বদলে তুমি সংসার থেকে যা পেয়েছিলে, সেকথা বুঝে এই সিদ্ধান্তে আমার আসতে কোনো ভুল হয়নি।
দাবি এ সংসারে কারও ওপরেই অন্যের কিছুমাত্র থাকে না। কিছু লোক মনে করেন যে, যেহেতু কেউ পারেন, যেহেতু ভগবান তাঁকে অন্যদের চেয়ে ভাগ্যবান করেছেন, সে ভগবানেরই গুণ; সেই হেতুই তাঁর বুঝি দায়িত্ব আছে ভাগ্যহীনদের ভার লাঘব করার।
এই বিশ্বাসে তুমি অনেকের দায়িত্ব হাসিমুখে বয়ে বেড়িয়েছ চিরটাকাল, সারাজীবন। অথচ খুব কমক্ষেত্রেই তার পরিবর্তে বিন্দুমাত্র কৃতজ্ঞতা আমি দেখেছি, তাঁদের বেশির ভাগেরই কাছ থেকে।
কোনো মানুষ যখন অন্য কারও জন্য কিছু করে, তখন তার মতো মানুষ হয় না। কিন্তু করতে করতে একটা সময়ে যখন বহুবিধ কারণে সেই করে-যাওয়াটা আর সম্ভব হয় না, সেই মুহূর্তে সেই মহৎ মানুষকে নীচ, স্বার্থপর, ইতর বলতেও সেই অনুগ্রহপ্রাপকদের বিন্দুমাত্র দ্বিধা হয় না।
.
১৩.
তর্পণ বা তিলাঞ্জলির মন্ত্র জানি না আমি।
তাই, তোমার কথা বলতে বসে, তোমার স্মৃতিচারণ করতে বসে, কত কী যে এলমেলো কথা মনে আসছে ভিড় করে। আগের কথা পরে, পরের কথা আগে; সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। সান্ত্বনা এইটুকু যে, তবু তো তোমার কথা মনে করার মতো অবকাশ ও আনন্দ আমার আছে।
কলকাতায় তুমি একদিন আমাকে বলেছিলে যে, যে কারও ওপর নির্ভর করে, বা যে কাউকে ভালোবাসে, তার নির্ভরতা বা ভালোবাসার কখনো অমর্যাদা করতে নেই।
আমার বোন মিনু ছেলেবেলায় অনেকটা তোমার মতো ছিল। বড়ো হয়েও সে অনেকানেক ব্যাপারে তোমার মতোই হয়েছে; চেহারাতেও। তার ফর্সা রং, গোল গাল হাত পা, মিষ্টিমুখ সব মিলিয়ে ভারি সুন্দর ছিল সে।
মিনু বড়ো দাদা-ভক্ত ছিল। আমার একটা ফেলে দেওয়া পুরোনো নটি-বয় শু ব্লেড দিয়ে কেটে কেটে তাকে বাড়িতে পড়ার চটি বানিয়ে দিয়েছিলাম আমি। সে চটি যে, কত লোককে মিনু দেখিয়ে বেড়াত তা কী বলব। বলত, দাদা দিয়েছে।
তখন বাটা কোম্পানি যে নটি-বয় শু তৈরি করতেন, সেইরকম জুতো আজকাল আর দেখি না। সে জুতো সমস্তরকম চেষ্টা করেও একবছর প্রতিদিন পরেও ছিঁড়ে ফেলা যেত না। স্কুলে যাতায়াতের পথে যাই-ই পেতাম, ডাবের খোলা, ইট পাটকেল সবকিছুতে লাথি মারতে মারতে যেতাম, যাতে তাড়াতাড়িতে জুতো ছেড়ে; নতুন জুতো পাই! তবুও কি সে জুতো হেঁড়ে! এত অত্যাচার সয়েও সে জুতো বছর ঘুরে এলেও ছিঁড়তে চাইত না।
মিনুকে নিয়ে একদিন বাজারে গেছি, দুপুরবেলা গরমের ছুটির সময়ে। আমার হাতে-হাত ধরে, গুটি গুটি পা-ফেলে ছোটোবোনটি আমার, আমার সঙ্গে গেছিল। খুবই ছোটো ছিলাম, তবুও তখন থেকেই হয়তো জানতে পেরেছিলাম, যাকে ভালোবাসা যায়, তাকে ভয় পাওয়ানোতে বা কম-বেশি পীড়ন করার মধ্যেও একটা তীব্র আনন্দ আছে। সে আনন্দ, সুস্থ কি অসুস্থ, সে-কথা এখানে অবান্তর। কিন্তু একজন আমাকে ভালোবাসে বলেই, আমার হাত ধরে সে পরমনিশ্চিন্ত বোধ করে বলেই, তার হাত থেকে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে, তার নিশ্চিন্ত থেকে তাকে বাইরে টেনে নিয়ে এসে একটা ভীষণ মজা পেতাম।
এই মজার নেশায় মজে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর অনেককিছু হারাতে হয়েছে জীবনে। কিন্তু খেলা মাত্রই হার জিতের। হারা অথবা জেতার মধ্যেই সব খেলার মজা। যে হারার ভয়ে ভীত হয় তার বোধ হয় কোনো খেলাই খেলা হয়ে ওঠে না।
সে জন্যে আপশোস নেই কোনো।
সারি সারি আলুর দোকান, বাজারে। তার পাশে ডিমের দোকান, সবজির দোকান। মিনু একমনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ডিমের আর মুরগির দোকানের সামনে খাঁচার মধ্যে মুরগিগুলোকে দেখছিল।
তখন ও খুব ছোটো ছিল, হয়তো বয়েস হবে পাঁচ কি ছয়। ও এত মনোযোগের সঙ্গে মুরগিগুলো দেখছিল যে, আমি সেই অবকাশে তাড়াতাড়ি ওর পাশ থেকে সরে গিয়ে আলুর দোকানের আড়ালে চুপটি করে দাঁড়িয়ে রইলাম। কিছুক্ষণ পর এদিকে-ওদিকে তাকিয়ে আমায় দেখতে না পেয়ে মিনু দাদা, দাদা, দাদা করে কাঁদতে কাঁদতে এমন করে চারধারে দৌড়োদৌড়ি করতে লাগল যে, ওর নরম গাল বেয়ে জলের ধারা নামল।
ওকে কাঁদিয়ে দারুণ এক নিষ্ঠুর আনন্দ পাচ্ছিলাম আমি কিন্তু তবু লুকিয়েই থাকলাম। যখন ও প্রায় ভয়ে পাগলের মতো দিশেহারা, তখন আমি আড়াল থেকে বেরিয়ে বললাম, এই মিনু, এইতো আমি!
আমাকে দেখতে পেয়ে রাগে, অভিমানে আনন্দে আরও জোরে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে মিনু দৌড়ে এসে আমার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল।
আমার এই ইচ্ছা করে হারিয়ে যাওয়ার কথা মিনু বাড়ি গিয়ে তোমাকে বলে দিয়েছিল।
তুমি আমাকে বকেছিলে। বলেছিলে, এ অত্যন্ত অন্যায়।
তারপরই তুমি জীবনে আমাকে প্রথম অভিশাপ দিয়েছিলে।
বলেছিলে, তুই কারুর ভালোবাসা ধরে রাখতে পারবি না।
সে কথার মানে তখন বুঝিনি। আজ অনেক বছর পেরিয়ে এসে, অনেক ভালোবাসা পেয়ে, অনেক ভালোবাসা হারিয়ে, অনেক ভালোবেসে তার বদলে নিষ্ঠুর হৃদয়হীন স্বার্থপর শৈত্য বুকে বয়ে আজকে বুঝি যে, তোমার সেই অভিশাপ কত বড়ো সত্যি ছিল।
এখনও মাঝে মাঝে ছেলেবেলারই মতো ইচ্ছে করে হারিয়ে যেতে, এবং এক বা একাধিকজনকে হারিয়ে দিতেও ইচ্ছে করে।
কিন্তু একজন দায়িত্ববান প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের পক্ষে হারানো কখনোই আর সম্ভব হয় না। পৃথিবী থেকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও হারিয়ে গেলেও তাকে তার ঠিকানাতে ফিরে আসতেই হয়। ঠিকানার শিকলে আমি বড়ো মূক, নিরুচ্চার একঘেয়ে বাঁধা আছি, ঘেউ-ঘেউ না-করা অবসরপ্রাপ্ত কুকুরের মতো।
আজ আর ইচ্ছা করলেই হারানো যায় না, ইচ্ছা না করলেও নয়।
এরকমই একটা অভিশাপ তুমি পরেও দিতে আমাকে, যখন আমি যুবক।
পড়াশোনা শেষ। জীবন সবে শুরু করেছি। যখন বহু বহু গণ্যমান্য ভদ্রলোকেরা তাদের সুন্দরী গুণবতী কন্যাদের পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করার জন্যে তোমাকে এবং বাবাকে অনুরোধ করছেন, অনবরত সেইসময় তোমার সঙ্গে আমার প্রায়ই ভুল বোঝাবুঝি হত।
তুমি সেই সময় বলেছিলে যে, তুই কোনো একজনকে নিয়ে জীবনে কখনো সুখী হতে পারবি না। তোর বিয়ে করাই উচিত নয়। তুই আজকে যা চাস, তা পাওয়া হয়ে গেলে, তা অবহেলায় ধুলোয় ফেলে দিস। পরের দিনই নতুন কিছু চেয়ে বসিস তুই। এইরকম যার মন, যে নিজে নিজেকে জানে না, যার নিজের মনের স্থিরতা নেই তার পক্ষে বিয়ে করা কখনোই উচিত নয়। তোর কোনো অধিকারই নেই কোনো মেয়েকে বিয়ে করে তাকে অসুখী করার।
বলেছিলে যে, তুই সুখী হবি না জীবনে।
তখন আমি জানিনি কিন্তু পরে জেনেছিলাম যে, মায়ের আশীর্বাদের মতে, অভিশাপও জীবনে ফলে।
তুমি মা, তাই হয়তো আমাকে বুঝেছিলে। গুণে এবং দোষে।
এরপরে সেই তুমিই, হয়তো মা বলেই বহুদিন আমাকে বলেছিলে; পরজন্মে যেন তোর মতো স্বামী পাই। কেন যে, সে কথা বলতে তা তুমিই জানতে।
এর মানে এই নয় যে, তুমি তোমার নিজের বিবাহিত জীবনে কোনোরকম অসুখী ছিলে। কিন্তু হয়তো এর মানে এই যে, অন্যের প্রতি যা সহানুভূতি, সমবেদনা এবং যা-বোধ আমার বুকে জমা করে রেখেছিলাম, পরিবর্তে কিছু পাই আর নাই-ই পাই; সেইরকমের অনুভূতি হয়তো তোমাদের যুগের সম্পূর্ণ পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের পুরুষদের মধ্যে সচরাচর অনুপস্থিত দেখা যেত।
তা ছিল সে যুগের প্রকৃতি।
জীবনে কোনো মানুষই সম্পূর্ণ সুখী হয় না। প্রত্যেক সুখেরই, চাঁদেরই মতো হয়তো দুটি পিঠ থাকে। বিশেষ কোণ থেকে দেখলে, এক বিশেষ বেলায় সেই সুখের এক পিঠে আলো পড়লে তাকে সুখ বলে মনে হয়। আবার অন্য কোণ থেকে দেখলে পড়ন্ত বিধুর গোধূলির আলোয় তাকে দেখলে তাকেই আবার অসুখ বলে মনে হয়।
জীবনের মধ্যেই সুখ দুঃখ সবকিছু মাখামাখি হয়ে, জড়াজড়ি করে থাকে।
তুমি কখনো বিষণ্ণ বোধ করলে একটা গান গাইতে নিজের মনে। গানটা ছিল টপ্পার কাজের গান। জানি না, নিধুবাবুর টপ্পা কি না। খালি গলায়ও তুমি গাইতে। পরবর্তী জীবনে অর্গান বাজিয়ে গাইতে রবীন্দ্রসংগীত। বেশির ভাগই ব্রহ্মসংগীত। কিছু অতুলপ্রসাদের গান। কিন্তু আজকেও সেই বিশেষ গানের কলিগুলো অস্পষ্ট মনে পড়ে বার বার ফিরে ফিরে।
সেই কথাগুলির গভীরতা, ছেলেবয়েসে হৃদয়ংগম করার বুদ্ধি আমার ছিল না। কিন্তু এই পরিণত বয়েসে পৌঁছে হৃদয়ংগম করি কী গভীর সেই কথাগুলি। টপ্পার কারুকাজ ভরা গানটি বিস্তার করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সমে পৌঁছোতে অনেক দেরিতে এসে।
তুমি গাইতে
আমি সুখী হলে তুমি সুখী হও;
তথাপি সুখের লাগিয়া হেথা রও!
সুখের উপরে দুখ, যার দুঃখ তার সুখ।
আমি অপরাধী ওগো, অপরাধী;
তবু আমারে চাহিয়া সুখী হও!
আমি দুখী হলে তুমি সুখী হও।
বোনেদের পরে আমাদের এক ভাই ছিল তার নাম বাবলু। দেখতে সে বিশেষ ভালো ছিল না। কালো-কোলো, নাকচোখও খুব একটা তীক্ষ্ণ নয়; কিন্তু সে বড়ো শান্ত ভালো ছেলে ছিল। কী মিষ্টি করে দাদা দিদি বলত। আমাদের পায়ে পায়ে ঘুরত!
একদিন স্কুল থেকে ফিরেছি। ফিরেই শুনলাম, বাবলুর বসন্ত হয়েছে। তখনকার দিনে বসন্ত, আসল বসন্ত বড়ো সাংঘাতিক অসুখ ছিল।
মা বাবলুকে নিয়ে মধ্যের ঘরে থাকলেন সেদিন থেকে। বাবাও সে-ঘরেই রইলেন। বোনেরা বাইরের ঘরে চলে এল।
কবিরাজ মশাই এলেন, কলাপাতায় মাখন নিয়ে। সেই মাখন বাবলুর সারাগায়ে কী এক প্রক্রিয়ায় লাগিয়ে দিলেন। সারাদিনই প্রায় নিমপাতা আর গন্ধক পোড়ানো হত। তার তীব্র কটু গন্ধে নাক ভরে থাকত আমাদের। অনেক ওষুধ-পত্র।
সে বছরে ছোটোদের কোনো পুজোসংখ্যায়, একটা গল্প প্রকাশিত হয়েছিল, গল্পটির নাম এতবছর পরে মনে নেই। কিন্তু তারমধ্যে একটা গল্পের একটা লাইন ছিল : মানুষ মরণশীল।
তখন থেকেই পড়ার বইয়ের চেয়ে বাইরের বই-ই বেশি পড়তাম। তবে বাইরের বই পেতাম না বেশি। আমাদের বাড়ির পাশেই একটি বইয়ের দোকান ছিল, সেই দোকানের মালিকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল আমার বড়োমামা। দোকানদারের একটি চোখ ছিল পাথরের। তাঁরই দয়ায় দোকানে গিয়ে গোগ্রাসে বই পড়তাম। অনেক সময় উনি বলতেন, নিয়ে যাও, মলাট দিয়ে পড়ে আমাকে আবার ফেরত দিয়ে যেয়ো। তাই বইয়ের, বিশেষ করে বাংলা বইয়ের অভাব হত না।
বাবলুর অসুখের মধ্যে, একদিন দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার পর ছুটির দিন, বাথরুমে আঁচাতে আঁচাতে হঠাৎ নিজের মনে বলে উঠেছিলাম মানুষ মরণশীল।
এই লাইনটা আমার মাথায় ছিল। কেন ছিল এবং কেনই বা খেয়ে-দেয়ে উঠে আঁচাতে আঁচাতে আমার মনে পড়ে গেছিল এবং মনে পড়ে গেলেও কেন যে তা জোরে জোরে বলেছিলাম সেকথা সেদিন যেমন জানিনি, আজও জানি না।
তার ঠিক তিনদিন পরেই রাত সাড়ে দশটা-এগারোটার সময় বাবলু আমাদের ছেড়ে চলে গেল। সন্ধে থেকেই অবস্থা খারাপ হয়েছিল। বাবা-কাকাদের দৌড়োদৌড়ি হুটোপাটি ডাক্তার কবিরাজ সবরকম চেষ্টা, এবং ঠাকুমার ক্রমাগত হরির নামের মধ্যেই বাবলু চলে গেল।
মা ভীষণ কাঁদতে লাগলেন।
বাবা আমাদের ডেকে বললেন, তোমরা বাবলুকে দেখে যাও, আর দেখতে পাবে না।
আমরা তিন ভাই বোন ভয়ে ভয়ে পা টিপে টিপে মধ্যের ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ালাম।
বাবলুকে আর দেখতে পাব না একথা তখন ভাবার মতো বুকের জোর ছিল না। দেখি সেই হাসিখুশি ভাইটি আমাদের, মুখটা কীরকম যেন হয়ে গেছে, সমস্ত মুখটা ফুলে ফুলে উঠেছে, চেনা যাচ্ছে না বাবলুকে। শরীরটা কীরকম ছোট্ট হয়ে গেছে। তুমি ওকে বুকে নিয়ে ভীষণ কাঁদছ।
তুমি কিন্তু মা কোনোদিনও জোরে কাঁদতে না। তোমাকে কোনোদিনও জোরে কাঁদতে দেখিনি। তোমার মুখ দিয়ে দুঃখের অভিব্যক্তি যদি প্রকাশিত হত তা খুব কম লোকই শুনেছে।
তুমি কাঁদছিলে, তোমার মুখ হাঁ হচ্ছিল, চোখ দিয়ে জল বেরোচ্ছিল, একটা অব্যক্ত শব্দও হচ্ছিল, কিন্তু তুমি চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কিছুই বলছিলে না।
কিছুক্ষণ পর বাবা-কাকারা বাবলুকে নতুন কাপড় জড়িয়ে বল হরি হরিবোল করতে করতে কেওড়াতলার দিকে নিয়ে গেলেন।
আমার জীবনে সেই প্রথম মৃত্যুর অভিজ্ঞতা।
তার পরদিন সকালে তুমি আমাকে ডেকে পাঠালে।
সে-ঘরে তখনও নিমপাতা ও গন্ধকের পোড়া গন্ধ, ওষুধ-বিষুধ কবিরাজি টোটকা সব পড়ে রয়েছে! বাবলুর ছোটো ছোটো প্যান্ট, জামা ওর ছোটো চটি, সবই আছে, সব।
শুধু ও-ই নেই। ]
মা বললেন, খোকন, তোকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব?
আমি বললাম, বল।
মা বললেন, তুই পরশুদিন দুপুরবেলা হঠাৎ বললি কেন যে, মানুষ মরণশীল?
আমার বুকটা হঠাৎ ভয়ে কেঁপে উঠল। আমারই কোনো অপরাধে হয়তো বাবলুর মৃত্যু হল! কেন বলতে গেলাম ওকথা? আমি কেন হঠাৎ না জেনে না বুঝে একথা জোরে বললাম, আর তার এত পরেই-বা কেন বাবলু চলে গেল?
আমি ভাবলাম, আমাকে বাবা-মা হয়তো খুবই বকবেন! হয়তো আমাকেই বাবলুর মৃত্যুর জন্য দায়ী করবেন।
দারুণ ভয় পেয়ে বললাম যে, না মা, তোমাকে দেখাচ্ছি। একটা বইয়ে পড়েছি মা। এখুনি বইটা আমি নিয়ে আসছি।
বলেই, দৌড়ে আমি পাশের ঘরে গিয়ে, সেই বার্ষিক সংখ্যাটি থেকে, সেই গল্পটি বের করে মা ও বাবা দুজনকেই দেখালাম।
কার লেখা গল্প, সেটি আজ আর মনে নেই। বোধ হয় খগেন মিত্র মহাশয়ের। এবং মানুষ মরণশীল একথা কোন পরিপ্রেক্ষিতে বলা হয়েছিল, তাও বোধ হয় মনে নেই। কিন্তু মানুষ যে মরণশীল একথা আমার ছোটোভাইয়ের মৃত্যুতে এমন করেই সেদিন বুঝেছিলাম যে, পরে সে সম্বন্ধে আর কোনোরকম ভুল বোঝার সম্ভাবনা ছিল না।
প্রত্যেক মানুষকেই একদিন না একদিন চলে যেতে হয় রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধ-স্পর্শভরা এই সুন্দর পৃথিবী থেকে। অথচ প্রতিটি মুহূর্ত আমরা কী আশ্চর্যভাবে এই কথাটা ভুলে থাকি!
তুমি নিজেও যখন ছিলে তখন একমুহূর্তের জন্যে কোনোদিনও মনে হয়নি যে, তুমি একদিন সত্যিই থাকবে না। মা বাবা যে চিরদিনই থাকেন না, একথা মা বাবা থাকতে বোধ হয় কোনো ছেলে-মেয়ের মনে একবারও আসে না।
স্মৃতি, কতসব সুন্দর দিন! কত হাসি কত গল্প কত ছোটো-বড়ো ঘটনা সব ফিরে ফিরে মনে আসে তোমাকে ঘিরে।
কলকাতায় বোমাপড়া আরম্ভ হল। একদিন বাইরের ঘরের দরজা খুলে সেজোকাকুর পাশে দাঁড়িয়ে দেখলাম, উদীয়মান সূর্য-আঁকা জাপানি প্লেনগুলো গোঁ গোঁ করে ঘুরে ঘুরে কলকাতার মাথার উপর চক্কর মারছে। বোমাও পড়তে দেখলাম সকালের পরিষ্কার রোদ্দুরে। চিকচিক করে উঠছিল রোদে, উপর থেকে যখন আস্তে আস্তে পড়ছিল বোমাগুলো।
বিকেলবেলা শোনা গেল খিদিরপুরে অনেক বোমা পড়েছে। খিদিরপুর ডকে। কলকাতা থেকে পালানোর হিড়িক পড়ে গেল। যাঁদের না থাকলেই নয়, ব্যাবসা অথবা চাকরির কারণে; শুধুমাত্র, তাঁরাই রয়ে গেলেন কলকাতার বুকে। জমি বাড়ি সব জলের দামে বিক্রি হতে লাগল। সবাই বলতে লাগল জাপানিরা এসে পড়ল বলে। সেইসময় বাবা আমাদের পাঠিয়ে দিলেন রংপুরে। আমাদের গ্রামের বাড়িতে।
.
১৪.
তোমার ছেলেবেলা কেটেছিল বিহারের এক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাঙালি-গরিষ্ঠ শহরে। জলে ভয় পেতে তুমি। গ্রাম কাকে বলে জানতে না। তোমার সাপের ভয়, বিছের ভয় এমনকী ভয়, টাকা-কেন্নোতেও। সেই যে বড়ো বড়ো বাদামি কেন্নোগুলো, টোকা মারলে টাকার মতো গোল হয়ে যেত, সেগুলো দেখলেই তুমি কী আতঙ্কে চিৎকার করে উঠতে। আর ভয় ছিল তোমার আরশোলাতে। সেই তুমিই ইকুয়েশানের সময় কলকাতার পাট চুকিয়ে রংপুরের বাড়িতে আমাদের নিয়ে থাকতে ঘোমটা টেনে, কতরকম গ্রাম্যতা মানিয়ে নিয়ে।
রংপুরের বাড়িতে চারটে ঘর ছিল। যে ঘরে আমরা থাকতাম তাকে বলা হত বড়ো ঘর। তারই নীচে বাঁশের ধারার ফলস-সিলিং। টিনের দেয়াল, তারমধ্যে অনেক ফুটো-ফাটা। তবে ভিত ছিল সিমেন্টের। মাটি থেকে অনেক উঁচু করে বাঁধানো। সে ঘরে আমরা ভাইবোনেরা, তুমি, আর ঠাকুমা শুতাম। সেই বড়ো ঘরের উলটোদিকে ছিল রান্নাঘর, মাটির ঘর, মাটির দেওয়াল, মাটির দাওয়া, মাটির সিঁড়ি। রান্নাঘরের ডানদিকে যে ঘর ছিল, তাতে থাকতেন বডোকাকু, তিনি বিয়ে করেননি। বড়োকাকুর ঘর পেরিয়ে ছোট্ট একটি ঘর। সেটি ছিল ঠাকুমার ঠাকুরঘর।
বড়োকাকুর ঘরের উলটোদিকে ছিল বাইরের ঘর। সেটিতে একপাশে বসার বন্দোবস্ত, অন্যপাশে ঢালাও তক্তপোশ পাতা। একসঙ্গে দশজন এসে পড়লেও কোনো অসুবিধা নেই।
সেই বাইরের ঘরের সামনেটায় ছিল প্রকান্ড গোলাপফুলের বাগান। কত যে গোলাপ ফুটত, সে বলার নয়। দূর দূর জায়গা থেকে লোকে আসত সে গোলাপবাগান দেখতে। বাগানের সামনে দিয়ে লালমাটির পথ চলে গেছিল। একদিকে খোঁয়াড়, শংকামারীর শ্মশান, অন্য দিকে শহর, ডিমলার রাজবাড়ির পাশ দিয়ে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের বাড়ির পাশ দিয়ে, জেলাস্কুলের সামনে দিয়ে।
গোলাপবাগানের পাশ দিয়ে ঘন সবুজ ঘাসে ঢাকা প্রায় পাঁচ-ছ কাঠা চওড়া আর বিঘে খানেক লম্বা ফালি জমি ছিল, সে জমি বেয়ে এসে বাড়ির ভেতরে ঢুকতে হত।
সে জমির বাঁ-দিকে ছিল বাগান, বিরাট বাগান, গোলা কাঁঠালের গাছ, জলপাই গাছ; কতরকম আম।
শীতকালে হলুদ জলঢোঁড়া সাপ রোদ পোয়াত সেই বাগানে। সেই বাগান যেখানে শেষ হয়েছে তারপরে ছিল আলুখেত। সেও বিরাট। একপাশে দাঁড়িয়ে অন্যপাশ অবধি চোখ পৌঁছোত না। সেই আলুখেতের পাশ দিয়ে চলে গেছিল ইরিগেশান ক্যানেল। সেই ক্যানেল গিয়ে পড়েছিল ঘোঘোট নদীতে; আর সেই নদী গিয়ে পড়েছিল তিস্তায়।
বর্ষায় যখন বান আসত তিস্তা নদে, ঘোঘোট নদী ভরে উঠত জলে। আর ঘোথঘাটের জল উপছে যেত ক্যানেল বেয়ে। ক্যানেলের জল এসে পুকুর দিত ভরে, বাদামি-কালো ডাহুক ডাকত সারাদিন ছায়াচ্ছন্ন পুকুরপাড়ে ঘুরে ঘুরে, তাদের শ্যাওলা শ্যাওলা শরীরে কাঁপন তুলে। সাদা-বাদামি বকগুলোঠায় একপায় দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজত আর কত কী ভাবত। বকেরা সারাদিন কী যে অত ভাবে, ভাবতাম আমি।
বাড়িতে ঢোকার রাস্তায় দু-পাশে দুটো কাঠটগরের গাছ ছিল। বড়ো গাছ। যখন ফুল ফুটত গন্ধে ম ম করত চারপাশ। হাসনুহানার ঝোঁপ ছিল, বাতাবিলেবুর গাছ। কাগজিলেবুর গাছ। রান্নাঘরের পেছনে অনেকখানি অব্যবহৃত জমি। তাতে মানকচুর ঝাড়, আশপাশে গজিয়ে উঠত বর্ষার দিনে কতরকম ব্যাঙের ছাতা। টকপাতার গাছ। কখনো কখনো বা সে ছাতার নীচে ধ্যানগম্ভীর ছাই রঙা ব্যাং থাকত বসে।
সেই ফালি জমিটুকুর পাশে ছিল কুয়োতলা। বিরাট বাঁধানো কুয়ো। কুয়োতলার গা ঘেঁষে একটা সিঁদুরে আমের গাছ। কালবোশেখির ঝড় উঠলেই ধপাধপ আম পড়ত ঝরে। কী তাদের রং! যেন কেউ সিঁদুর মাখিয়ে দিয়েছে।
বড়ো ঘরের ডানপাশে ছিল ঠাকুমার হবিষ্য ঘর। মাটির ওপরে শন ছাওয়া। তার পাশে চেঁকিঘর। তারই পাশে গোয়ালঘর। গোয়ালঘরে থাকত ফুলমণি গাই আর তার বাছুর। গোখরো সাপ এসে কখনো কখনো ফুলমণির পা জড়িয়ে ধরে ফুলমণির দুধ খেয়ে যেত চুরি করে। রাতের বেলায় আসত বাদুড়ের ঝাঁক। লিচুগাছে লিচু খেয়ে যাবার জন্যে। তখন বাদুড় তাড়াবার জন্যে লিচুগাছে কেরোসিনের টিন বেঁধে তাতে লাঠি ঝুলিয়ে লাঠির দড়ি ধরে টানাটানি করত সারারাত আমাদের নেপালি দারোয়ান বাহাদুর। বাদুড় তাড়াবার জন্য।
কাঁঠাল গাছের পাতা ঝরে ঝরে পড়ত মাটিতে–শান্ত, পাখি-ডাকা কাঁচপোকা-ওড়া দুপুরে গোবর নিকোনো উঠোনে। কত তাদের রং। সোনালি, গাঢ় বাদামি, হলুদ। গরমের দুপুরে হাওয়ার গন্ধ, মাঠের গন্ধ, পাতার গন্ধ, গোবর-নিকোনো উঠোনের গন্ধ, হলুদ বসন্ত পাখির গায়ের গন্ধের সঙ্গে মিশে যেত।
শেষ-বিকেলে চেঁকিতে পাড় দিতে তুমি। এখনও মনে পড়ে, তোমার সেই ছিপছিপে সোনারঙা চেহারা, লালপেড়ে শাড়ি পরেছ তুমি, তোমার লক্ষ্মীমন্ত পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়েছে শাড়ির পাড়, আর চেঁকির একপ্রান্তে তুমি দাঁড়িয়ে আছ ওপরে ঝোলানো দড়ি ধরে। আর নামছ উঠছ, উঠছ নামছ।
চিড়ে কুটতে কখনো। শব্দ হত বুক ধুক; ধুক বুক। তালে তালে স্বর মিলিয়ে সেই বাদামি ল্যাজঝোলাবড়ো পাখিটা বাইরের বাগানে ডেকে চলত গুব গুব; গুব গুব।
কলকাতা থেকে বাবা তোমাকে চিঠি লিখতেন নীলরঙের খামে, মোটা মোটা চিঠি। বিকেলে স্নান করে, চুল বেঁধে, সিঁদুরের টিপ পরে, তুমি বারান্দার এক সিঁড়িতে বসে অন্য সিঁড়িতে পা রেখে সে চিঠি পড়তে।
চিঠি পড়তে পড়তে তোমার মুখের ভাব সেই সুন্দর সুগন্ধি বিকেলের মতো নরম হয়ে উঠত। কত কী পাখি ডাকত চারদিকে।
আস্তে আস্তে আকাশের রং গোলাপি হয়ে যেত। আকাশ যখন পরিষ্কার থাকত, তখন উত্তরে কাঞ্চনজঙ্ঘার চুড়ো দেখা যেত। আমি হু-হুঁ হাওয়ায় খোলা মাঠে দাঁড়িয়ে স্বর্গসরণির সাদা মেঘপুঞ্জের সঙ্গে মিশে যাওয়া কাঞ্চনজঙ্র রুপোলি চুড়োর ওপরে শেষ সূর্যের গোলাপি রঙের খেলা দেখতে দেখতে বিস্ময়ে আনন্দে শিহরিত হয়ে উঠতাম।
কখনো কখনো তুমি রাঁধতে বসতে রান্নাঘরে। সামনে কুপি জ্বলত। কিন্তু উনুনের আগুনের আভায় রান্নাঘর ভরে থাকত। উনুনের সামনে বসে তোমাকে দেখাত দেবী প্রতিমার মতো উজ্জ্বল।
খেতের লাল মিষ্টি চালের ভাতের গন্ধ ভাসত মন্থর সান্ধ্য গ্রাম্য হাওয়ায়, শেয়াল ডাকত ক্যানেলের ধারে, পেঁচা আর বাদুড় ঝুপ-ঝাঁপ করত ঝোপে-ঝাড়ে। নির্জনতাকে চমকে দিয়ে তক্ষক ডাকত নারকোল গাছের গোড়ার ঝোঁপ-ঝাড় থেকে।
বাবা যখন কলকাতা থেকে মাঝেমধ্যে আসতেন দু-তিনদিনের জন্যে, তখন বলতেন যে, ভাতের ফ্যান মোটে গালবে না। ফ্যানের মধ্যে কত ভিটামিন! কলকাতায় কত লোক একটু ফ্যান দাও মা, ফ্যান দাও মা বলে কেঁদে মরছে।
কিন্তু তুমি রোজই সে কথা ভুলে যেতে। অন্যমনস্ক হয়ে ভাতের ফ্যান গালতে। বাবা পিচবোর্ডের ওপরে কাগজ সেঁটে তাতে বড়ো বড়ো করে লিখে দিয়েছিলেন ভাতের ফ্যান গালিবে না এবং সেই পিচবোর্ডে লেখাটা উনুনের পেছনের দেওয়ালে, বাঁশের খুটিতে পেরেক দিয়ে মেরে দিয়েছিলেন। রান্না করার চৌকিতে বসে সে লেখাটা যাতে চোখের সামনেই থাকে।
কিন্তু তা সত্ত্বেও তুমি দু-একদিন ভুলে যেতে, ভাতের ফ্যান গালতে।
রান্নাঘরের পাশে যে কাগজিলেবুর গাছটা ছিল, সেই লেবুতে এত রস হত যে, বাহাদুর বলত কুইয়া কা পানি। সেই লেবুর গন্ধ এখনও নাকে লেগে আছে।
খেতের চালের ভাত, খেতের আলুভাজা, আর তাতে কাঁচালঙ্কা ডলে আর সেই লেবু চিপে কাঁঠাল কাঠের পিঁড়িতে বসে মাটির রান্নাঘরে বসে যে ভাত খেতাম, সে ভাতের স্বাদ পৃথিবীর বহু শ্রেষ্ঠ শহরের শ্রেষ্ঠতম হোটেলের খাওয়ার ঘরে বসেও পাইনি।
রংপুরে বড়ো মাছ বিশেষ পাওয়া যেত না। তুমি আবার ছটো মাছ একেবারেই খেতে পারতে না। ছোটো ছোটো পুকুরের কুচোকাঁচা মাছ, গরমের দিনে কই, শিঙি পুকুর-হেঁচা; শীতকালে পুঁটি, খয়রা, বাটা এইসব। তুমি বেঁধে দিতে, বড়ো ভালো রান্না করতে তুমি; কিন্তু সেই ছোটোমাছ খেতে পারতে না কখনো। খেলেও, ভালোবেসে খেতে না।
খাবার কথা উঠলে কত কথাই যে মনে পড়ে, শীতের কি বর্ষার রাতে তোমার ভুনি খিচুড়ি, সেই খিচুড়ি রান্না তুমি শিখেছিলে দিদিমার কাছ থেকে।
দিদিমা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শিষ্যা ছিলেন। গিরিডিতে প্রতিসপ্তাহে তাঁর গুরুভাইরা এসে জমায়েত হতেন বাড়িতে। বিকেলে মোহনভোগও হত। সেইরকম মোহনভোগও তুমি আমাদের বেঁধে খাওয়াতে। এমন মোহনভোগ আর কখনো খাব না। কড়া করে সুজি ভেজে, ভালো করে ঘি ঢেলে, লবঙ্গ, দারচিনি দিয়ে কী অপূর্ব মোহনভোগ যে তুমি রাঁধতে, সে যে না খেয়েছে, তার পক্ষে বোঝাই মুশকিল।
খিচুড়িতে কড়াইশুঁটি দিতে। ভাজা মুগের ডালের খিচুড়ি। বেশি পাতলাও নয়; আবার খুব ঘনও নয়। কী যে তার স্বাদ! সঙ্গে শুকনো লঙ্কা ভাজা, কড়কড়ে করে আলু ভাজা, ডিম ভাজা। তোমার খিচুড়ির গন্ধ এখনও নাকে লেগে আছে। কত জায়গায়ই তো খিচুড়ি খাই, কিন্তু অমন খিচুড়ি আর কেউই রাঁধতে পারে না।
আর তোমার কড়াইশুঁটির চপ? কীভাবে যে করতে, তা তুমি একাই জানতে। যাবার আগে কাউকে একটু শিখিয়েও গেলে না! তুমি আমাদের ভালোবাসতে না ছাই! ভালোবাসলে মানুষ ভালোবাসার জনদের এমন করে হঠাৎ ফেলে চলে যায়?
কড়াইশুঁটির চপের পুরটার একটা আলাদা বিশেষত্ব ছিল, আর বিশেষত্ব ছিল চপের ওপরের আবরণের। সেই চপ যেই-ই খেয়েছে আমাদের বাড়িতে, সেই-ই প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছে।
মাঝে মাঝে ঠাট্টা করে তোমাকে বলতাম, পড়াশোনা করে আর কী হবে তোমার চপের রেসিপিটা শিখিয়ে দাও, একটা দোকান দেব রাসবিহারী অ্যাভিনিউয়ে, খালি এই চপেরই। গাড়ির পর গাড়ি এসে লাইন করে দাঁড়িয়ে থাকবে আমার দোকানের সামনে। চপ বেচেই বড়োলোক হয়ে যাব।
তুমি কথা শুনে হাসতে।
বলতে, তা আর করবি না? চপ বিক্রি করেই তো খাবি!
খাবার কথা ভাবলে আরও কত কথা যে মনে হয়, তোমার রান্নার কথা। ইলিশ মাছ রাঁধতে তুমি কতরকম, ভাপা-ইলিশ, দই-ইলিশ; কালোজিরে সরষে দিয়ে ইলিশের ঝোল। হলুদ রঙা।
সরস্বতী পুজোর দিন দুপুরবেলায় আমরা যেখানেই থাকি না কেন, আমাদের বাড়িতে জোড়া-ইলিশ রান্না হতই। তখনকার দিনে সারাবছর ইলিশ মাছ খাবার রেওয়াজ ছিল না। প্রতিবছর ইলিশ মাছ খাওয়ার মহরত হত সরস্বতী পুজোর দিনে জোড়া-ইলিশ লাউডগা দিয়ে রান্না হত। পাতলা ঝোল, কালোজিরে কাঁচালঙ্কার সঙ্গে। সে ঝোলের স্বাদ এখনও মুখে লেগে আছে। আর সরস্বতী পুজোর রাত্রিবেলা প্রত্যেক বছরই হত খিচুড়ি। তেমনি কালীপুজোর দিন রাত্রে হত লুচি-মাংস।
মাংসই বা কতরকম করে রাঁধতে জানতে তুমি! অমন হলুদ-রঙা টক-মিষ্টি-ঝাল স্বাদু দই মাংস আর খাই না! সেই মাংসের ঝোল দিয়ে থালা থালা ভাত খেতাম আমরা। চিতল মাছ, চিতল মাছের মুঠা, চিতল মাছের পেটি, কইমাছ, সরষে কই, ধনেপাতা কাঁচালঙ্কা দিয়ে তেল-কই, রুইমাছের দইমাছ, রুইয়ের কালিয়া আরও কত কী রান্না!
বাবার এক বন্ধু ছিলেন, তাঁর বাড়ি ছিল চট্টগ্রামে। তাঁরই প্ররোচনায় বাবা একদিন শুঁটকি মাছ এনে হাজির করলেন। সকলের প্রাণ যায় যায় অবস্থা।
বাড়িওয়ালা আমাদের বাড়ি ছাড়ার নোটিশ দেওয়ার উপক্রম করলেন।
কিন্তু কে শোনে কার কথা?
বাবা বললেন, হোল-সাম ফুড। ফুল অফ প্রোটিন। এত লোকে খায়, আর যারা খায়, তারা কত খাটতে পারে জানো? ভালো করে পেঁয়াজ রসুন দিয়ে রান্না করো। আগে জলে সেদ্ধ করে নাও, কিছু গন্ধ থাকবে না।
তুমি বাবার কোনো ব্যাপারেই কোনোদিন আপত্তি করতে না।
আঁচলের এককোনায় একটু অগুরু ঢেলে, সেই আঁচল নাকের সামনে ধরে তুমি সেই শুঁটকি মাছ রান্না করলে।
প্রথম দিন বাবা একাই খেলেন, তুমি তো ছুঁলেই না, আমরাও ধারেকাছে গেলাম না। অথচ তখন বাবার শাসন অগ্রাহ্য করি, এমন সাহস আমাদের কোনো ভাই-বোনেরই ছিল না। এটা খাব না, ওটা খাব না, এইসব বায়নাক্কা কোনোদিনও বাবা প্রশ্রয় দেননি।
একদিন মিনু বলেছিল, নিমপাতা খেতে ভালো লাগে না।
বাবা বলেছিলেন, মনে করো, এমন একটা দেশে গেলে, যেখানে খালি নিমপাতারই গাছ। নিমপাতা ছাড়া আর অন্য কোনো গাছই নেই। না সেখানে ধান খেত, না কোনোরকম ডাল পাওয়া যায়, না অন্যকিছু, তখন তুমি কী করবে? তুমি কি না খেয়ে থেকে মরে যাবে? না নিমপাতা খাবে?
মুখ বিকৃত করেও মিনুকে নিমপাতা খেতে হয়েছিল।
বাবার কড়া শাসনে আমাদের তিন ভাই-বোনের মধ্যে কারোরই এই ডাল খাই না, ওই মাছ খাই না এইসব প্রেফারেন্স গড়ে ওঠার কোনো সুযোগই হয়নি।
যাই হোক, সেই প্রথম দিনের শুঁটকি পর্বর পর থেকেই বাবার পীড়াপীড়িতে মাঝে মাঝেই বাড়িতে শুঁটকি মাছ আসতে লাগল। ঘোরতর পশ্চিমবঙ্গীয় বাড়িওয়ালা নেপথ্যে বলতে লাগলেন যে, বাঙালগুলোরজন্যে দেশছাড়া হতে হবে।
তখনও ভাগ্যিস দেশ ভাগ হয়নি।
শেষের দিকে মনে আছে, তুমি নিজেও বেশ তৃপ্তি করেই শুঁটকি মাছ খেতে এবং এমন উপাদেয় করে রান্না করতে যে কী বলব। পেঁয়াজ রসুন লঙ্কা দিয়ে ভালো শুঁটকি মাছ, ভালোভাবে রান্না করলে তা দিয়ে যে একথালা ভাত এমনিই খাওয়া যায় তা নিজে খেয়েই বুঝেছিলাম।
বহরমপুরের অনুপমকাকুর স্ত্রীর কাছ থেকে তুমি তাহেরি রান্না শিখে এলে। তাই নিয়ে চলল ক-দিন এক্সপেরিমেন্ট। তখন বাঙালি রান্না, এদেশীয় এবং পূর্ববঙ্গীয় এবং কিছু কিছু মোগলাই রান্নারই চল হয়েছে। চাইনিজ খাওয়া তখন কাকে বলে খুব কম লোকই তা জানতেন। স্বাধীনতার এত বছর পর আজ যেমন খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে একটা আন্তর্জাতিক রুচি গড়ে উঠেছে এবং স্বাধীনতার পরে যে দক্ষিণ ভারতীয় এবং উত্তর ভারতীয়, বিশেষ করে পাঞ্জাবের খাওয়ার-দাওয়া এত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে, আমাদের ছেলেবেলায় তা মোটেই ছিল না। কোনো নতুন রান্না কোথাও খেয়ে এলে, কী কোথাও তার খবর শুনে এলে তোমার এবং বাবার সে বিষয়ে উৎসাহের অন্ত থাকত না।
.
১৫.
আমাদের বিভিন্ন বাড়িতে কত যে, আত্মীয়-স্বজনের বিয়ে হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। বছরে দু-তিনটে করে বিয়ে লেগেই থাকত। তখনকার দিনে নাওড়ি-ঝিয়োরিরা এসে বিয়ের আগে থেকেই উপস্থিত হতেন। এক-একটা বিয়ে মানে, এক-এক মাস বাড়ি-ভরতি লোকজন, অঢেল খাওয়া-দাওয়া, অনির্বাণ চিতার মতো উনুন জ্বলা আর পড়াশোনার বড়োই অসুবিধা।
আগেই বলেছি, পূর্ব-বঙ্গীয় যৌথ-পরিবারের অনেক কিছুই ভালো, কিন্তু ছোটো ছেলে মেয়েরা বড়োই অনাদৃত সেখানে। তাদের পরীক্ষা আছে কি নেই, তাদের পড়াশোনার ঘর আছে কি নেই, এ নিয়ে কাউকে মাথা ঘামাতে দেখিনি।
কত আত্মীয় স্বজনের বিয়ে হয়েছে, আজ তাঁরা কোথায় কোথায় চলে গেছেন। বিভিন্ন জায়গায় ঘর সংসার পেতেছেন। হয়তো ইচ্ছা থাকলেও যোগাযোগ আর নেই। কলকাতায় যদিও বা তাঁরা আসেন হয়তো আমাদের বাড়িতে তাঁরা আসেনও না; সময়ও হয় না।
হয়তো সত্যিই হয় না।
মানুষের জীবন এরকমই। যে যার নিজের ঝামেলা, নিজের যন্ত্রণা নিজের ঝক্কি নিয়েই আছে। কিন্তু যোগাযোগ থাকুক আর নাই থাকুক, আমাদের সমস্ত আত্মীয়-স্বজন, যাঁরা তোমাকে জানতেন, তোমার কাছে ছিলেন কখনো, তোমার মধুর ব্যবহারে যাঁরা সিঞ্চিত হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজনও যে তোমাকে আজও মনে করেন না, এমন হতেই পারে না।
তুমি নইলে কোনো বিয়ের সম্বন্ধ হত না। যদি আমাদের বাড়িতে কোনো আত্মীয়াকে বরপক্ষ দেখতে আসতেন, তুমি নইলে সে আত্মীয়ার মা-বাবা অত্যন্ত নার্ভাস হয়ে পড়তেন। তুমি ছিলেন বলে যে কত বিয়ে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছিল বিয়ের সময় যে কত অপ্রিয় ঘটনা ঘটতে ঘটতে ঘটেনি সেকথা যাঁরা জানেন, তাঁরাই জানেন।
কেউ তোমাকে মামিমা বলতেন, কেউ বলতেন মাসিমা, কেউ বলতেন কাকিমা, কেউ বলতেন পিসিমা, কেউ বলতেন বউদি, যে যে-নামেই ডাকুক না কেন, তুমি সকলের কাছেই ছিলে সমান প্রিয়।
আজকে তোমার অবর্তমানে বাবার সমস্ত সম্পদ, সুন্দর সাজানো বাড়ি, সাজানো বাগান, সব যেন খাঁ খাঁ করে। মনে হয় লক্ষ্মী চলে গেছে এ-বাড়ি ছেড়ে। তোমার শ্রীহস্তের ছোঁয়া আর যেন কিছুই পায় না এ বাড়ি।
প্রতিবছর চৈত্র সংক্রান্তির আগে আগে তুমি নিজে দাঁড়িয়ে সারাবাড়ি পরিষ্কার করাতে, ঝুল ঝাড়াতে; সবকিছু নতুন হত। পয়লা বৈশাখের আগে আগে কোনো ছুটির দিনে সকালে বাবা ও তুমি একই সঙ্গে নিশ্চয়ই নিউ মার্কেটে যেতে। আমার বরাদ্দ ছিল প্রতিবছর নববর্ষে আমার ঘরের জন্যে নতুন একটি পাপোশ এবং সুন্দর একটি বেডকভার।
তুমি চলে যাবার পর পয়লা বৈশাখকে আর পয়লা বৈশাখ বলে মনে হয় না। সারাবাড়ির চাকর-বাকর, লোকজন, মায় কুকুর-বেড়াল, সকলেই তুমি নেই বলে কেমন মনমরা হয়ে থাকে।
বাড়িতে যা কিছুই রান্না হত-না-কেন, তুমি সব থেকে আগে, চাকর-ঠাকুর কী খাবে, তাদের ভাগটা আলাদা করে তুলে রাখতে। ড্রাইভার তার ডিউটি শেষ করে যত রাতই হোক না কেন, যখন বাড়ি যেত, তুমি তাকে নিজে ডেকে জিজ্ঞেস করতে যে, সে খেয়েছে কি না। এবং যদি তার খাবার সময়ে তুমি নিজে না দেখতে পেতে, তাহলে ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করতে কী খেয়েছে সে।
তুমি চলে গেছ বলে, ওরা যত দুঃখী হয়েছে, তেমন দুঃখী আর কেউই হয়নি। জন্তু জানোয়ার তারাও ভালোবাসা বোঝে, তারাও বোঝে কোন মানুষটা কোন চোখে তাদের দিকে তাকায়, কোন মানুষটার অন্তরে তাদের প্রতি কী অনুভূতি আছে; আর আমরা তো মানুষ। তোমার স্নেহ, তোমার মমতা, তোমার ভালোবাসা যারা পেয়েছে। তারা তোমার কথা কি এত সহজে ভুলতে পারে?
আমি চিরদিনই একটু অন্যরকম ছিলাম। সে কারণে, তুমি প্রায়ই আমাকে ভুল বুঝতে। নানা ব্যাপারে তোমাকে আমি খ্যাপাতাম, তোমার আমাদের নিয়ে ভয়, উৎকণ্ঠা, সবসময় তোমার আঁচলে আড়াল করে রাখার চেষ্টা এইসব নিয়ে।
প্রায়ই তোমাকে বলতাম হাসতে হাসতে, সাত কোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননী। রেখেছো বাঙালি করে মানুষ করোনি।
বাঙালি মায়ের দোষ অনেক। সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু যে সেই মা-হারা হয়; সেই-ই জানে তার গুণ।
তিনখানার ওপরে যেদিন বাবা চতুর্থ গাড়ি কিনলেন, সেদিন আমি আমার ডাইরিতে লিখেছিলাম, তোমার বকে যাওয়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত প্রবল। তুমি কখনোই শুধু যেন বাবার পরিচয়েই পরিচিত হোয়ো না। সংসারে যার নিজের পরিচিতি নেই, যে বাবা-মামা কাকা জ্যাঠার পরিচয়েই পরিচিত থাকে সে মানুষই নয়।
এই পাশ্চাত্যদেশীয় মনোবৃত্তি তুমি বরদাস্ত করতে পারতে না। বাবাও পারতেন না। হয়তো আজকেও আমার এই স্বাধীনচেতা মনোভাব এবং ব্যক্তিত্বে বিশ্বাসী প্রকৃতি এবং আত্মসম্মানবোধ পুরোপুরি মেনে নেওয়া হয়তো বাবার পক্ষে সম্ভব হয়নি।
আর তুমি তো ভুল বোঝাবুঝির ওপারেই চলে গেছ।
স্কুল ফাইনাল পাস করার পর বাবা বললেন, বাড়িতে বসে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে মোটা হবে, তার চেয়ে আমার অফিসে আসবে, পঞ্চাশ টাকা মাইনে পাবে। কাজ শেখো।
তোমার কড়া শাসনে আমি তখনও এমনই ক্যাবলা ছিলাম যে, আট নম্বর বাসে উঠে যখন অফিসের দিকে রওনা হলাম, তখন চৌরঙ্গির মোড়টা ঠিক কোথায়, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ ছিলাম না।
একটা বড়ো মোড় দেখে যখন নেমে পড়লাম এবং বাসটা চলে গেল, তখনই বুঝলাম যে এটা চৌরঙ্গি নয়। একটা ঝাঁকা মুটে তার ঝাঁকার ওপর বসে বিশ্রাম করছিল, তাকে বললাম, ভাই, এই জায়গাটার নাম কী?
সে বলল, ওয়েলেসলি বা।
আমি বললাম, ধর্মতলা কোনদিকে যাব?
সে বলল, যে বাস থেকে নেমেছিলেন, সেই বাসেই তো ধর্মতলা যাবেন।
তখন আবার সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে বাসের অপেক্ষায় সময় কাটল কিছুক্ষণ। তারপর আবার বাস এলে ধর্মতলায় পৌঁছোলাম।
আরও বেশ কিছুদিন পর আমি তখন কলেজের ছাত্র, তুমি পুজোর সময় আমাকে দুশো টাকা দিলে। বললে, খোকন, তুই খুশিমতো জামাকাপড় কিনে নিস।
আমি তোমাকে বললাম, আমি তো অনেক বড়ো হয়ে গেছি আর রোজগারও করছি। এখন আর আমাকে এমন করে টাকা দিয়ো না। টাকা চাই না আমি। বরং বাবাকে বোলো, যদি বাবা মনে করেন, তাহলে আমার মাইনে একটু বাড়িয়ে দিতে। বড়ো হয়ে যাবার পর হাত পেতে টাকা নিতে লজ্জা করে।
তুমি পুরোপুরি বাঙালি মায়েরই মতো তোমার দুর্বিনীত ছেলের কথাতে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললে।
বললে, তাহলে তোর বাবা এত টাকা কেন রোজগার করেন?
আমি বলেছিলাম, সেকথা তুমি বাবাকেই জিজ্ঞাসা কোরো। সেকথা আমার জানার নয়। কিন্তু বাবার রোজগারের টাকাতে আমার কোনো অধিকার নেই; এবং সে-টাকা নিতেও রাজি নই।
জানি না, হয়তো তুমি চলে যাবার আগে আগে বুঝেছিলে কি না, যে, তুমি আমাকে যতখানি অবাধ্য ভাবতে, যতখানি দুর্বিনীত ভাবতে, আমি ঠিক ততখানি ছিলাম না।
হয়তো অন্যরকম ছিলাম, কিন্তু সেটা তোমাদের অপমান করার জন্য নয়।
হয়তো অন্য দেশে জন্মালে আমার এই মানসিকতা, অন্যের প্রশংসার দাবি রাখত।
যেহেতু আমি এই দেশে জন্মেছিলাম, যেহেতু এই দেশে এইরকম মানসিকতা সাধারণ ছিল না, বিশেষ করে ওই সময়ে; সেইহেতু আমাকে চিরদিনই ভুল-বোঝাবুঝির শিকার হতে হয়েছে।
তুমি যে কত বুঝদার ছিলে! তোমার জন্য কিছুমাত্র করতে গেলে, তুমি সব সময় বলতে, না না। থাক থাক। তোর কত অসুবিধা, তোর কত খরচ, তুই এত টাকা দিবি আমাকে? আমার জন্য তুই এত ভালো শাড়ি কিনলি?
আমি বলতাম, তোমাকে দেব না তো কাকে দেব?
তোমার কাছ থেকেই শিখেছিলাম যে, শুধু মা বাবাকে নয়, সবাইকে দেওয়ার আনন্দ কী! বিনা-স্বার্থে, বিনা-কারণে কারও জন্যে কিছুমাত্র করার সমস্ত আনন্দটুকুই যে করে তা যে তারই একার।
এই অকৃতজ্ঞ হিসেবি, ভন্ড, চক্ষু-লজ্জাহীন জগতে তোমাকে লোকে বোকা বলত।
বলে, আমাকেও।
কিন্তু যে চক্ষুলজ্জাহীন ভন্ড মানুষরা তা বলে, তাদের হাসিমুখে ক্ষমা করার ক্ষমতাও তুমিই দিয়েছিলে।
জীবনে যা পেয়েছি, ভবিষ্যতে যাই-ই পাব, তার সমস্তটুকুই তোমারই দেওয়া। তোমার প্রত্যেকের প্রতি নিষ্কলুষ শুভকামনায় ভরা, আতরগন্ধি অন্তরের ঔদার্যের কারণে।
সেই আমার একমাত্র উত্তরাধিকার।
তুমি উইল করে কিছুই দাওনি আমাকে। দিলেও নিতাম না আমি।
কিন্তু যা তুমি দিয়েছিলে, সেই সম্পদ অমূল্য। সে সম্পদ সকলে অন্তরে ধরে রাখতে জানে না। সকলের অন্তরে ভগবান সে ঔদার্য দেনও না।
এ সংসারে গরিব সেজে থাকা, কৃতজ্ঞতা অস্বীকার করা, টাকা পয়সাকেই পরমধন বলে জানাই বুদ্ধিমানের লক্ষণ।
আমি সেই অর্থে বুদ্ধিমান নই। তুমি আমাকে সেই দুর্বুদ্ধি দাওনি কোনোদিন। তোমার কাছে আমি এ কারণে আজীবন, অশেষ কৃতজ্ঞ।
কাউকে কিছু দেওয়ার, দিতে পারার আনন্দ যে কী, কতখানি; তা সেইসব ভন্ড মানুষরা, সাবধানি অর্থগৃধু মানুষেরা কখনো জানল না, জানবেও না।
একটা কথা ভেবেই আমার বড়ো দুঃখ হয় যে, আমাকে তুমি খুবই ভালোবাসতে বলেই আমার দ্বারা তুমি অনেক দুঃখ পেয়েছ।
আজকে তুমি নেই। আমার ব্যাখ্যা হয়তো কোনো প্রয়োজনে লাগবে না তোমার। তবু আমার বিবেকের কারণে, আমার নিজের কাছে নিজেকে জবাবদিহি করার কারণে আমি একথা বলা প্রয়োজন মনে করি।
সংসারে অনেক দুঃখই মানুষকে পেতে হয়। আর্থিক দুঃখ, পারমার্থিক দুঃখ, এরমধ্যে কোনো দুঃখ অন্যর চেয়ে বড়ো অথবা ছোটো নয়। যে দুঃখ আমাদের পেতে হয়ই, তার কিছু কিছু আমাদের নিজেদেরই কৃতকর্মের ফল। কিন্তু এমন অনেক দুঃখ পেতে হয়, যার জন্য আমরা নিজেরা দায়ী নই।
যেসব দুঃখ আমার কারণে তুমি পেয়েছিলে, তার জন্য তুমি নিজে বিন্দুমাত্র দায়ী ছিলে না। অথচ দুঃখ তোমাকে পেতেই হয়েছিল। তোমার সেই পুরোনো গানের কথাতেই বলি, যার দুঃখ, তার সুখ, সুখের উপরে দুখ।
যে মানুষ দুঃখ সইতে না জানে, যে মানুষ দুঃখ এবং আনন্দকে সমান কৃতজ্ঞতার সঙ্গে জীবনে স্বীকার করতে না জানে, সে মানুষই নয়।
এ তো তোমারই শিক্ষা, তুমিই তো আমাকে এই কথা শিখিয়েছিলে, তাই মাঝে মাঝে যখন মাঝরাতে ঘুম আসে না, একা জানলার পাশে দাঁড়িয়ে তারাভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবি, তুমি কি সুখে আছ?
অথবা তুমি কি সব দুঃখের দুয়ার পেরিয়ে গিয়ে এক প্রগাঢ় আনন্দের জগতে বাস করছ?
নাকি শরীরের খাঁচা থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত হবার পরও আত্মার দুঃখ থাকে?
তখনও কি আত্মা প্রিয়জনের দুঃখে কাতর হয়, তখনও কি তার পুরোনো আবাসের কাছাকাছি সে ঘুরে বেড়ায়?
যখন খুব ঝড় ওঠে, প্রচন্ড বৃষ্টি পড়ে বজ্রপাত হয়; তখন ভাবি তুমি কোথায় আছ?
তুমি কি বিদ্যুৎ চমকে ভয় পাচ্ছ? তুমি বড্ড ভয় পেতে বাজ পড়লে। বাচ্চা মেয়ের মতো।
তোমার মাথায় কি ছাদ আছে মা? মহাশূন্যের ঘরের জানলা-দরজাগুলো ঝড় ওঠার আগে তোমার চুড়ি-পরা সোনার বরণ আঙুলে তুমি কি বন্ধ করে দিয়েছ?
না, তুমি এই দুর্যোগের রাতে ভিজে গিয়ে ঝড়ে-জলে অন্ধকারে শীতে কেঁপে উঠছ?
কিছুই জানি না। অথচ কত কিছুই জানি আমরা। আমরা জানি মানুষ চাঁদে পা দিয়েছে, আমরা জানি মানুষের মগজ বাইরে বের করে এনে মানুষের মগজে বড়ো বড়ো সার্জেনরা অপারেশন করছেন।
আমরা জানি যে, শিগগিরই ক্যান্সারের ওষুধ বেরোবে।
আমরা জানি যে, পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষ, কিন্তু এদের মধ্যে একজনও অন্যের মতো নয়, নয় শরীরে, নয় মনে।
আমরা জানি এক মা-বাবার একাধিক সন্তান হয়, অথচ তারাও কেউ নয় একে অন্যের মতো, নয় মনে। নয় স্বভাবে।
তাইতো ভগবান বিশ্বাস করি।
বিজ্ঞান শুধু আবিষ্কারই করে, বিজ্ঞান কিছুই উদ্ভাবন করে না।
যা তাঁরই ছিল, যা তাঁর দান, যা তাঁরই সৃষ্টি, তাকেই ভাস্কো-ডা-গামার মতো পালতোলা নৌকোয় চড়ে গিয়ে মানুষ আবিষ্কার করে, এবং আবিষ্কার করে মিথ্যা উদ্ভাবনের আত্মশ্লাঘায় বেঁকে ওঠে।
যদি আমাদের পুণ্য আত্মার মৃত্যু না হয় কখনো তবে তুমি নিশ্চয়ই আছ আমার কাছেই, দিনের আলোর উজ্জ্বল উদ্ভাসের গভীরে উদবেল অন্ধকার রাতের তারারা যেমন থাকে!