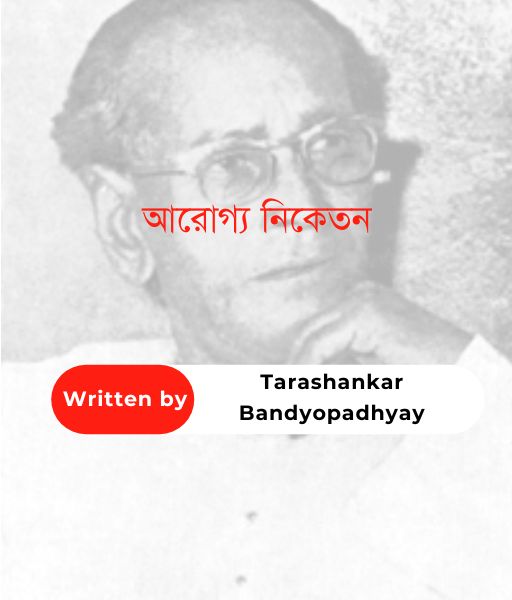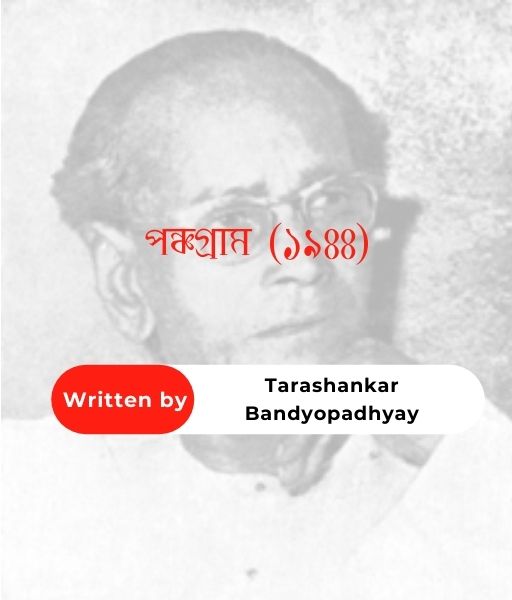দ্বিতীয় খণ্ড – চতুর্থ পর্ব : ৪.১৫
পরের দিনের সন্ধ্যা—সুলতাকে সামনে রেখে সুরেশ্বর বললে।
—আজ আমার মুলতুবী জবানবন্দী আরম্ভ করতে গিয়ে আমাকে পিছিয়ে যেতে হচ্ছে সুলতা। ১৮৫৭ সালে বীরেশ্বর রায় এসেছিলেন কীর্তিহাটে। তখন মিউটিনির সময়। পিছিয়ে যাচ্ছি ১৮১৫-১৬ সালে বীরেশ্বর রায়ের জন্মের আগে।
না গেলে, যে গোপন পাপ রায়বংশের রক্তের ধারায় বয়ে চলছে, পুরুষ থেকে পুরুষান্তরে তার কথা বলা হবে না। সেইটে বলব।
যে কথা সযত্নে গোপন করে গেছেন রত্নেশ্বর রায়, যার আভাস মাত্র দিয়ে ডায়রীতে স্পষ্ট লিখেছেন—“সে কথা লিখিতে পারিব না! সজ্ঞানে মৃত্যু হইলে এই ১৮৬০ সালের ডায়রীখানি আমার চিতায় দগ্ধ করিতে বলিব।” সেই গোপন কথা আমি পেলাম পুলিশের খানাতল্লাশির সময়—যখন তারা খাস কাছারীর কাঠের সিন্দুকভর্তি চিঠিপত্রের দপ্তর বা ফাইলগুলো কাঁকড়াবিছের ভয়ে তছনছ করে দিয়ে গেল।
এক কথায় তত্ত্বের খোলে মুড়ে বলতে পারি—সে পাপ ধর্মজীবনের ছিদ্র দিয়ে প্রবেশ করা পাপ, আর সম্পদ এবং সংসারজীবনের মধ্যে বাসা বাঁধা পাপ। কিন্তু তাতে গুরুত্বটা ঠাওর করা যাবে না। কি ঘটেছিল তাই বলতে হবে।
সোমেশ্বর রায়ের কন্যা বিমলার বিয়ে দিয়েছিলেন সন্ন্যাসী শ্যামাকান্তের পুত্রের সঙ্গে। বিমলাকান্তের সঙ্গে। তার কারণ, তান্ত্রিক সন্ন্যাসী শ্যামাকান্তরই কি সব তান্ত্রিক ক্রিয়াকর্মের ফলেই সোমেশ্বর রায়ের স্ত্রী রাজকুমারী কাত্যায়নীর সন্তান হয়ে বেঁচেছিল এবং শ্যামাকান্ত একদিন দুর্যোগের রাত্রে নৌকো করে কীর্তিহাটের ওপারে জঙ্গলের মধ্যে সিদ্ধপীঠ সাধনভজন ক’রে ফিরবার পথে নৌকোডুবি হয়ে ভেসে যান। সোমেশ্বর রায় তাঁর সঙ্গে ছিলেন, তিনি ভক্তি এবং আগ্রহবশে শ্যামাকান্তের শিষ্য হিসেবে সঙ্গে থাকতেন; নৌকোডুবির পর অনুতাপ হয়েছিল তাঁর যে, তিনি বাঁচলেন আর গুরুর মত শ্যামাকান্ত বাঁচলেন না, তাঁকে তিনি বাঁচাতে পারলেন না।
পাপ এঁদের দুজনের। ধর্মের পাপ এই শ্যামাকান্তের। আর সংসার সম্পদের পাপ সোমেশ্বরের। মাতৃবংশ আর পিতৃবংশ। রত্নেশ্বর রায় থেকে দুই পাপ যুক্তধারায় চলে আসছে রক্তের স্রোত ধরে পুরুষানুক্রমে ধারা রেখে। ওইখানেই ব্যাধির মূল।
সুলতা বাধা দিলে। বললে—পাপ-পুণ্য এসব বাদ দিয়ে বল। তাঁদের পাপ-পুণ্যের বিচার নাই করলে। তাঁদের পরের পুরুষরা যা করেছে সে দায়িত্ব তাদের। পূর্বপুরুষের ঘাড়ে চাপিয়ে লাভ কি বল! হেরিডিটি যদি বল, তবু মেনেও বলল—হ্যাঁ, দায়িত্ব পরবর্তী পুরুষদের।
সুরেশ্বর একটু চুপ করে থেকে বললে, হেরিডিটি অমোঘ, ও এড়ানো সহজে যায় না। সে চেহারা থেকে মুদ্রাদোষ থেকে চরিত্র পর্যন্ত সব। কিন্তু তাই শুধু আমি বলছি না। ওই পাপ-পুণ্যই আমি বলব। আমি বিশ্বাস করেছি। তার কারণ, যে চিঠিগুলি পেয়েছি তার বিবরণ থেকে আমি বিশ্বাস করেছি, এমন পাপ আছে যাতে সৃষ্টির, মহাপ্রকৃতির অভিসম্পাত পড়ে। মানুষের উপর পড়ে, বংশের উপর পড়ে। তাছাড়া বাস্তব সংসারের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় এক পুরুষের কর্মের ফল অন্য পুরুষকে ভোগ করতে হয়। তাও তো হারায় না সংসারে! রায়বংশের পূর্বপুরুষের কৃতকর্মের ফল সেদিন গোয়ানপাড়ায় দেখে এসেছিলাম। তার কিছুদিন আগে অতুলেশ্বরের কেসে শিবু সিং বলে ছেলেটির অ্যাপ্রুভার হয়ে সাক্ষী দেওয়ার মধ্যে প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়েছি। ধর্ম ভগবান পাপ সেকালের মানুষের জীবনে প্রত্যক্ষ সত্য। কালকের জবানবন্দীর মুলতুবীর সময় এসেছিল, আজ তাই স্বাভাবিকভাবে উঠেছে। ও নিয়ে তর্ক করতে বসি নি। তুমিও করো না। তাহলে তর্কেই রাত্রি শেষ হবে। ধর্ম আর ভগবতীর সন্ধানে ১৮১৫ সালে শ্যামাকান্ত গৃহত্যাগ করেছিলেন।
সুরেশ্বর সেই বারান্দা-ঘেরা ছবির ঘরেই কালকের মত আলো জ্বেলে বসে তার প্রতীক্ষা করছিল। ছবিগুলোর দিকে তাকিয়েই সে বসেছিল। হাতে সিগারেট পুড়ছিল। সামনে টিপয়ে একটা শূন্য গ্লাস। সুলতা ঘরে ঢুকতেই সে বললে—এস।
সুলতা বললে—এলাম। কিন্তু অৰ্চনা, কই? তোমার ব্রজেশ্বরদা আছেন শুনলাম, তিনি?
সুরেশ্বর বললে—তারা কালীঘাট গেল, দর্শন করতে।
—ব্রজেশ্বরবাবু তো—
সুরেশ্বর বললে—হ্যাঁ অন্ধ। তবু মায়ের সামনে যাবে প্রণাম করবে। কাঁদবে। একটু চুপ করে থেকে বললে—মানুষটাই পাল্টে গেছে সুলতা। একমাত্র নিষ্ঠুর আঘাতই মানুষকে পাল্টায়। পাথর মানুষ ফেটে গিয়ে ঝর্ণা বের হয়, আবার জলভরা দীঘি বন্যার পর রাশীকৃত বলতে মজে গিয়ে মরুভূমি হয়ে যায়। রাজকুমারী বউ কাত্যায়নী দেবীর জন্যে যে পুকুর কাটিয়ে ঘড়া বিশেক দুধ ঢেলে দুধপুকুর নাম দেওয়া হয়েছিল, সেটা ১৯৪২ সালের সাইক্লোনে কাঁসাইয়ের বানে এমনিভাবে মজে বালির মরুভূমি হয়ে গেছে। ব্রজেশ্বরদা অন্ধ হয়ে, লাঠি ধরে ছেলে নিয়ে এক কীর্তিহাটে, সেটা আটচল্লিশ সাল। আমি খবর পেয়ে দেখতে গেলাম, তখন ও নাটমন্দিরে প্রণাম করছে, আর ঝরঝর চোখের জলের ধারায় ভাসছে। শান্ত করতে বললাম—ভয় কি ব্রজদা, আমি চিকিৎসা করাব তোমার, ভাল হয়ে যাবে চোখ। ও বললে কি জান? বললে-না-না, রাজাভাই না। চোখ আর আমার দরকার নেই রাজাভাই। চোখ গিয়ে আমি কাঁদতে শিখেছি। কান্না ভুলে যাব। অনেক হেসেছি রাজাভাই, অনেক। জীবনটাকেই হাসিকৌতুক করে নিয়েছিলাম। কান্নার সুখ জানতাম না। এ বড় সুখ। চোখ আর আর আমি চাই না! আমার ধনেশ্বরকাকা ব্রজদার বাপ, তিনি অ্যাক্টিং করে কথা বলতেন। ব্রজেশ্বরদা সেদিন বিল্বমঙ্গল থেকে আবৃত্তি করেছিল—“ভেবে দেখ মন, কত তোরে নাচায় নয়ন।” শুনে আমারও চোখে জল এসেছিল সুলতা। মনে হয়েছিল—গোটা রায়বংশের অন্তরাত্মা যেন আবৃত্তি করছে।
সুলতা এসেছিল একরকম মন নিয়ে। মনটা তার আর একরকম হয়ে গেল। ব্রজেশ্বর কেমনভাবে আবৃত্তি করেছিল তা সে শোনে নি। কিন্তু ওর কথা যদি সত্য হয়, তবে তার ছোঁয়াচ যেন আজ সুরেশ্বরের কণ্ঠেও রয়েছে বলে মনে হল তার।
রঘু এসে চায়ের ট্রে নামিয়ে দিলে।
সুরেশ্বর বললে-গ্লাসটা নিয়ে যা। আর বলে দে, সুলতাও খাবে। অর্চনাদের ফিরতে দেরী হবে একটু। ওরা হয়তো খেয়েও আসতে পারে। কালীঘাট থেকে ওরা অতুলের বাসায় যাবে দেখা করতে।
সুলতা বললে—অতুল? ও, সেই অতুলেশ্বরকাকা তোমার?
—হ্যাঁ। সে তো এখন একজন লীডার। কতকগুলো সরকারী কমিটির মেম্বার। তার বাসা আছে। সে রায় লেখে না আর, লেখে ভট্টাচার্য।
—ও। জিঞ্জার গ্রুপের অতুল ভটচাজ? কিষাণ লীডার?
—হ্যাঁ। রায়বংশের রায় এবং ঈশ্বরত্ব সে বাদ দিয়েছে। কীর্তিহাটের সংস্রব সে রাখে না। এখন তিন-চারটে সরকারী কমিটির মেম্বার। পলিটিক্যাল সাফারার হিসাবে দুখানা ট্যাক্সি পেয়েছে। সে তার জীবন নতুন করে আরম্ভ করেছে। আসছে ইলেকশনে সে অ্যাসেম্বলীতে দাঁড়াবে।
সুলতা হেসে বললে–লোকে বলে, পুণ্যের ফল নাকি দেরীতে মেলে। কিন্তু আমি তো দেখছি, পণ্য যদি চেঁচিয়ে করে তবে তার ফল হাতে হাতে।
সুরেশ্বর বললে—সেটা পলিটিক্সের পুণ্য সুলতা। সে কি ট্রেজারী বেঞ্চের দলে, কি অপোজিশনে। ট্রেজারীর দলে নগদ বিদায় আছে, কিন্তু অপোজিশনে পজিশন আছে। ভগবানের রাজত্বে পাপ বল পুণ্য বল দুয়ের ফলই না পাকলে পড়ে না। কিম্বা ডিম থেকে বাচ্চা হওয়ার মত। যাক শোন, কালকে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত এসেছি। আজ কিন্তু পিছিয়ে আরম্ভ করতে হবে। ১৮১৫-১৬ সালে। রায়বংশের পাপের কথাটা বলব।
১৮১৫-১৬ সালে শ্যামাকান্ত ভট্টাচার্য নামক এক কুলীন সন্তান। তার প্রথম বয়সের ছবি নেই। প্রথম ছবি ওই দেখ কালীঘাটে, সোমেশ্বর রায়ের সঙ্গে। চোখে পাগল-পাগল দৃষ্টি, দাড়ি-গোঁফে ঢাকা মুখ। ঝাঁকড়া চুল। তখনই আধ-পাগল। পেশাদার কুলীনের ছেলে; অর্থাৎ বাপ কৌলীন্য মূলধনের জোরে যশোর অঞ্চল থেকে পশ্চিমবঙ্গে কুলীনের কন্যাদায় উদ্ধার করে বেড়াতেন। বছরে এক মাস পনের দিন এক এক শ্বশুরবাড়ীতে থেকে—গুরুর বাৎসরিক পার্বণী, পুজোর বাৎসরিক পার্বণ পিতৃ-পিতামহের একোদ্দিষ্ট-বড়দিনে জজ-ম্যাজিস্ট্রেট লাটসাহেবের ডালির মত তাঁদের পাওনা নির্দিষ্ট ছিল—কাপড় চাদর পাথেয় এবং নগদ দক্ষিণা নিয়ে চলে যেতেন। একটা স্বস্থান ছিল এবং একজন পত্নী জীবনসঙ্গিনী থাকতেন। কাশীকান্ত, -কাশীকান্ত ছিল শ্যামাকান্তের বাপের নাম। কাশীকান্তের যিনি ঘরণী-গৃহিণী, তাঁরই গর্ভের সন্তান শ্যামাকান্ত। কাশীকান্তের পেশা বিবাহ হলেও তিনি তন্ত্রমতে সাধনভজন করতেন। আর গানও তিনি গাইতে পারতেন।
কাল একথা বলেছি। তবু মনে পড়িয়ে দিচ্ছি। শ্যামাকান্ত ছেলেবেলা থেকে একটু যেন কেমন অস্বাভাবিক ছিলেন। কেমন একটা বাইরের নেশা ছিল। গ্রাম থেকে বেরিয়ে নদীর ধারে কিম্বা বনে জঙ্গলে ঘুরতেন! আর ছিল তাঁর গানের নেশা। ওই বিদ্যায় দখল নিয়ে তিনি জন্মেছিলেন। তেমনি ছিল কণ্ঠস্বর।
একটু হেসে সুরেশ্বর বললে-একাল হলে এ মানুষটি মিথ্যে তন্ত্রসাধনা করতে ছুটত না। পাগল হত না। সিনেমায় মিউজিক ডিরেক্টার হত। জীবনের কাম্য তাঁর এর মধ্যেই মিলে যেত।
হাসিটা মিলিয়ে গেল সুরেশ্বরের। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে—এই মানুষটির মত হতভাগ্য মানুষের জীবনকথা আমি পড়ি নি—কারুর কাছে শুনি নি, কল্পনাও করতে পারি নে। প্রথম যৌবনেই যখন বাপ মারা গেলেন, তখন তিনি পাখা মেললেন। গান গেয়ে বেড়ানো পেশা ধরলেন—আর তার সঙ্গে সাধন-ভজন। দীক্ষা বাপের কাছে নিয়েছিলেন। হঠাৎ মনে তন্ত্রসাধনার ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠল। এসে হাজির হলেন শ্যামনগরে, পদ্মনাভ ভট্টাচার্যের কাছে। বললেন—দীক্ষা আমার বাবার কাছে নিয়েছি। কিন্তু পুরশ্চারণ হয়নি; আমাকে, পুরশ্চারণ করিয়ে দিতে হবে। পূর্ণাভিষেক দীক্ষা দিতে হবে।
পুরশ্চারণ, পূর্ণাভিষেক না হলে শক্তিসাধনায় অধিকার হয় না।
পদ্মনাভ ভট্টাচার্য বললেন—এক সপ্তাহ থাক এখানে; আমি দেখি তোমার ওই অধিকার আছে কিনা। তারপর বলব।
সুন্দর সুপুরুষ চেহারা, নবীন বয়স। কথায়-বার্তায় উল্লাস। দুঃসাহসী। তার উপর তাঁর গান। মার্গসঙ্গীত, শ্যামাসঙ্গীত দুইই গান অপূর্ব। হা হা করে হাসেন। সারা রাত গান ক’রে ক্লান্তি নেই। শ্যামাসঙ্গীত—তখন রামপ্রসাদ সদ্য বিগত, বাংলাদেশ রামপ্রসাদের গানের স্রোতে ভেসে যাচ্ছে। কীর্তন গানে একসময় বাংলাদেশ ভেসেছিল। তেমনি করেই ভেসেছিল সে কালটা শ্যামাসঙ্গীতে।
সাত দিনের মধ্যে গোটা শ্যামনগর জয় করে নিয়েছিলেন শ্যামাকান্ত। তাঁর বয়সী নবীন দলের পাণ্ডা হয়ে উঠেছিলেন। মানুষটা বিচিত্র, যেখানে থাকে সেইখানটিকেই নিজের ঘর করে নিতে পারে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে। তাঁর নিজের সংকোচ নেই–অসংকোচ নবীন শ্যামাকান্ত গৃহস্থেরও সকল সংকোচ ভেঙে দেন। পদ্মনাভ ভটচাজকে একদিনেই ঠাকুরমশাই থেকে বাবাঠাকুর, দ্বিতীয় দিনে ‘বাবা’ বলতে লাগলেন, তাঁর গৃহিণীকে মাঠাকরুণ থেকে মা বলে আপনারা হয়ে গেলেন। পদ্মনাভ ভটচাজের এগার বছরের কুমারী কন্যা মহালক্ষ্মী তাঁর পরম ভক্ত হয়ে উঠল।
সাতদিনের দিন পদ্মনাভ বললেন—দেখ, তোমার লক্ষণ জন্মলগ্ন সব বিচার করে আমি দেখেছি বাবা কান্ত। তোমার ভাগ্য খুব জটিল। আবার সাধকের লগ্ন, লক্ষণ সব আছে। তোমাকে সস্ত্রীক সাধনা করতে হবে। ঘরে থেকে সাধনা করলে তুমি রামপ্রসাদের মত মাকে পাবে। স্বয়ং মা তোমার কন্যা হয়ে এলেও আসতে পারেন। আর সন্ন্যাসী হলে এ সাধনায় তোমার বিপদ আছে বাবা।
শ্যামাকান্ত নিজের হাতের রেখা দেখতে দেখতে বলেছিলেন—কি হবে?
—তা আমি দেখতেও পাচ্ছি না, বলতেও পারছি না। তবে হতে পারে অনেক রকম- উন্মাদ হতে পার; মহাশক্তি তো ছলনাময়ীও বটেন, তাঁর ছলনায় যে কত রকম হয়—
শ্যামাকান্ত বলেছিলেন—তা হোক, তার সঙ্গে খেল্ খেলতে গিয়ে পাগল হলে না হয় হব! তবে তাকে তো আমার পিছু পিছু ফিরতে হবে?
পদ্মনাভ বললেন—একটা কথা বলি বাবা, শোন। তুমি আমার মহালক্ষ্মীকে বিয়ে কর। ওর ভাগ্য খুব ভাল। তবে ওর পরমায়ু স্বল্প। তা হোক, ওকে বিয়ে করে তোমরা সস্ত্রীক পুরশ্চারণ কর, পূর্ণাভিষিক্ত হও; তোমার মন্ত্র আমি জেনেছি। এই তো?
ব’লে কানে কানে তাঁর দীক্ষার বীজমন্ত্রটি উচ্চারণ করেছিলেন, শ্যামাকান্ত চমকে উঠে- ছিলেন। পদ্মনাভ ভট্টাচার্য বলেছিলেন—ওকেও আমি ওই মন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে রেখেছি। কুমারী হলেও দিয়েছি। ওর ভক্তিযোগ প্রবল। তোমার বাবা ভক্তিযোগ খামতি। জ্ঞানযোগ, মানে ক্রিয়া-কাণ্ডে আসক্তি প্রবল। তুমি এমন শ্যামাসঙ্গীত গাও শুনে অন্যজনে কাঁদে, তুমি কাঁদ না। ও তোমার সঙ্গে থাকলে দুটোর মিল হবে। কল্যাণ হবে তাতে। সিদ্ধি পাবে। আমারও এই এক মেয়ে, আমার যজমান পাবে, লাখরাজ পাবে, শিষ্যসেবক পাবে। বাবা, তোমাকে সোজা ক’রে বলি—কাঁদতে শিখতে হবে তোমাকে আগে। তা দেখ, ভক্তিতে কাঁদা সোজা কথা নয়। মায়ায় মমতায় শোকে দুঃখে নরম হতে হবে বাবা কান্ত। সন্ন্যাসী হলে যত শুকনো আছ, তার থেকেও শুকিয়ে যাবে। তখন আছাড় মেরে ভাঙলে তবে যদি জল বেরোয়, বুঝেছ!
শ্যামাকান্তের ভুরু কপাল সব কুঁচকে উঠেছিল। তিনি যেন ভাবতে শুরু করেছিলেন কথাটা।
পদ্মনাভ বলেছিলেন—একটা সত্য কথা বলবে বাবা?
শ্যামাকান্ত দৃষ্টি ফিরিয়ে তাঁর দিকে তাকিয়েছিলেন, কিন্তু ভুরু ললাটের কুঞ্চন মিলোয় নি। পদ্মনাভ বলেছিলেন-আমার কথায় রাগ হচ্ছে, নয়?
শ্যামাকান্ত এবার হেসে বলেছিলেন—তা হচ্ছিল।
—হ্যাঁ হবে, আমি জানি যে। এখন যে কথাটা জিজ্ঞাসা করব তার জবাব দাও তো বাবা!
—বলুন।
—রাগ না করে, বেশ ভেবে আমাকে সত্য কথা বলতে হবে।
—হ্যাঁ?
—বলুন!
—ধর, এই যে তুমি ঘুরে বেড়াও, হাস, গান কর, তোমার এমন রূপ, তোমাকে সবাই ভালবাসে। মেয়ে-পুরুষ বলতে গেলেই সবাই। তা বাবা। থেমে গিয়ে হেসে বলেছিলেন- রাগ করতে নেই আমার কথায়, আমাকে গুরু করতে এসেছ! বল তো মেয়েছেলেদের, বিশেষ করে যুবতী মেয়েদের দিকে তাকিয়ে কি ভাব তোমার জাগে? মনে মনে মা বলে—তার মুখ থেকে চোখ ফিরিয়ে মাটির দিকে তাকাও না।
শ্যামাকান্ত বেশ ভেবেই ঘাড় নেড়ে জানিয়েছিলেন—না।
—হুঁ। আমি জানি। তোমার লক্ষণে রয়েছে একথা। তা জান তো, চণ্ডীতে আছে—“স্ত্ৰীয়া সকলাঃ সমস্তা জগৎসু!” মহাপ্রকৃতি এই জগতের নারীপ্রকৃতির মধ্যেই নিজেকে প্রকাশ করে রেখেছেন। এদের মা বলতে পারলে তিনি মায়ের মত দয়া ঢেলে দেবেন—বুকে করবেন। না পারলে বাবা শিব হতে হবে—তাও শবরূপী শিব! না-হলে তিনি আঘাত করবেন। তোমার বুকে চড়ে ধেই ধেই করে নাচবেন। শেষ পর্যন্ত গ্রাস করবেন। এখন ভেবে দেখ তুমি।
সেদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত ভেবে শ্যামাকান্ত পদ্মনাভ ভট্টাচার্যের কথায় রাজী হয়েছিলেন। তাঁর কন্যা মহালক্ষ্মীকে বিবাহ করে শ্বশুরের কাছে তন্ত্রশাস্ত্রের শিক্ষা নিয়েছিলেন এবং তাঁকে ‘পটল গুরু’ করে পূর্ণাভিষিক্ত হয়ে পুরশ্চারণ করে ক্রিয়া-কর্ম শুরু করেছিলেন। খানিকটা শান্তও হয়ে এসেছিলেন। তবে ছিল গানের ঝোঁক! সেটা কমে নি, সেটা ক্রমশঃ বেড়েই চলেছিল। কোথাও কোন বড় ওস্তাদের খবর পেলে আর ঘরে থাকতেন না। ছুটতেন।
শ্বশুর পদ্মনাভ ভটচার্জ বারণ করতেন। বলতেন—বাবা, সিদ্ধি যদি চাও বাবা, তবে গান গেয়ে মাকে ডাক। বুঝেছ না? তুমি গাইবে, মা শুনবেন। বুঝলে! এই যে তুমি বড় বড় ওস্তাদের পেছনে ছোট, তাদের আসরে কেলোয়াতির মার-পেঁচ শোন, এর মধ্যে কেরামতি অনেক। লাঠির দুই মাথায় আগুন জ্বেলে খেলোয়াড়েরা খেল দেখায়, লোহার গোল বালায় ন্যাকড়া জড়িয়ে আগুন ধরিয়ে চারটে পাঁচটা নিয়ে লোফালুফি করে। সে কেরামতি বটে, কিন্তু তাতে রান্নাও হয় না, হোম-যজ্ঞিও হয় না, এমন কি বাবা তার আলোতে কাজকর্ম, রাত্রে আঁধারে পথ চলা তাও হয় না।
কিন্তু শ্যামাকান্ত ও কথা মানতে পারতেন না। আবার পঞ্চপর্বে-অমাবস্যায়-পূর্ণিমায়- চতুর্দশীতে-অষ্টমীতে-সংক্রান্তিতে মাঝরাত্রে উঠে চলে যেতেন। শ্মশানে জপ করতে।
এর মধ্যেই বছর তিনেক পর মহালক্ষ্মীর সন্তান হল। বিমলাকান্ত
শ্যামাকান্ত ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন। কই, কন্যা হল কই?
শ্বশুর বলেছিলেন—সময় হলে হবে বাবা! সাধনাতে অধীর হলে চলে? মা তোমাকে তো কৃপা করেছেন মনে হচ্ছে। আগে বংশধর দিলেন। এবার হবে।
এই সময়ে হঠাৎ জ্বরবিকারে মারা গেলেন পদ্মনাভ ভটচাজ। শ্যামাকান্ত এবার গুরুহীন হয়ে বাধাবদ্ধহীন হয়ে উঠলেন। তাঁর খেয়ালীপনা বাড়ল। মধ্যে মধ্যে শ্মশানচারী হতেন, মধ্যে মধ্যে গানের খেয়ালে মাততেন। গানের খেয়ালে মাতলে তখন বড় বড় জমিদার ধনীর বাড়ী গিয়ে উঠতেন, গান শোনাতেন। গান শুনিয়ে শিরোপা নিয়ে ফিরতেন দু মাস তিন মাস পর।
শাশুড়ী পদ্মনাভ ভট্টাচার্যের গৃহিণী তখন নিজের কপালে ঘা মেরে বলতেন-এ কি কপালে ছিল মহালক্ষ্মীর! একটা লক্ষ্মীছাড়া বাউণ্ডুলের হাতে পড়েছে। ঘরের দেবসেবা অচল; যজমানের ক্রিয়া-কর্ম চলে না। শিষ্যরা মন্ত্র নিতে এসে ফিরে যায়—শেষ পর্যন্ত কি বড়-ভট্টচাজের পাট্ বন্ধ হবে! কপাল, আমার কপাল!
কন্যা মহালক্ষ্মীর তা গায়ে লাগত; এবং স্বামীর আচরণও তাকে আঘাত দিত। একটা নিদারুণ অবহেলা তিনি অনুভব করতেন স্বামীর আচরণের মধ্যে। কিন্তু শাস্ত মানুষ ছিলেন তিনি—তিনি নীরবে সব সহ্য করতেন।
তবুও ঝগড়া হত মধ্যে মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে। মহালক্ষ্মী মৃদুস্বরে বলতেন—শ্যামাকান্ত চীৎকার করতেন। এবং সে চীৎকারের মধ্যে একটা কথাই ফিরিয়ে ঘুরিয়ে বলতেন। শ্বশুর তাঁকে প্রতারণা করেছেন। কিন্তু এমন সাধু মোলায়েম বাক্যে নয়, একেবারে সে আমলের খাস চলতি কথায় বলতেন-বেটা আমাকে গরু ভেবে দড়িতে বেঁধে আটকে গেছে। বেটা জানত না, আমি গরু নই, আমি ষাঁড় নই, আমি মোষ—মহিষাসুর। খোলছানি মাড় খেয়ে বাঁধা আমি থাকবার নই। দড়ি যেদিন ছিঁড়ব, সেদিন তছনছ করে দেব সব। হ্যাঁ!
তাঁর সে মূর্তি দেখে শিউরে উঠতেন স্ত্রী মহালক্ষ্মী এবং তাঁর মা। শুধু তাই নয়, গৃহীর তান্ত্রিক আচরণ ত্যাগ করে তিনি বামাচারীর পথ ধরতে গেলেন। তান্ত্রিকের কন্যা মহা- লক্ষ্মীর কাছে এ অগোচর রইল না। তিনি কিছুদিন লক্ষ্য করে বললেন-এ কি হচ্ছে?
—কি? ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করলেন শ্যামাকান্ত
—কি? আমাকে ফাঁকি দিতে চাচ্ছ? আমি কিছু বুঝি না, না?
—বুঝেছিস তো বুঝেছিস।
—গুরুর দেখানো পথ ছাড়লে কি হয় জান না?
—জানি, কচু হয়।
—সে কচু গুরুর ভাগ্যে নয়, নিজের ভাগ্যে জোটে। গুরু তোমাকে যাকে মা বলে ভজনা করতে বলেছেন—তাকে তুমি শালী বলে গাল দাও!
—হ্যাঁ দিই। মা বললে সে মা-শালী বললে সে শালী। মা বলে ডেকে তো দেখলাম। করুণা? ধুর! করুণা চাইলে দেমাক বাড়ে। আর করুণা চেয়ে পাবটা কি? শালা মুষ্টিভিক্ষে। যা না, দশ বাড়ী ঘুরে কেঁদে আয় দেখ, মুষ্টিভিক্ষের বেশী কি মেলে? শালা মারি তো গণ্ডার লুটি তো ভাণ্ডার! বুঝেছি—জবরদস্তি চুলের মুঠো ধরে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে ওকে বশ না মানালে ও মানে না। শালা ওই পথ।,
শাশুড়ীকে বললেন—ও সব তোমাদের শুদ্ধাচারে পুজোটুজো আমার দ্বারা হবে না—তুমি পুরুত দেখ। দিগে বন্দী পুজো। শক্তি পাট বোষ্টুম পাট—তাও আবার শক্তি পাটে কালী দুর্গা জগদ্ধাত্রী পুজোতে সকাল থেকে তিন পহর পর্যন্ত বন্দী। লোক রাখ। ও আমার দ্বারা হবে না।
লোকের অভাব ছিল না সেকালে। ব্রাহ্মণেরা বিশেষ করে গৃহস্থ ঘর যাদের তারা ত্রিসন্ধ্যা করত, পূজাপাঠ করত নিত্যনিয়মিত। পদ্মনাভ ভটচাজের বংশের পেশা গুরুগিরি। তাদের প্রত্যেকের ঘরে ছিল শালগ্রাম শিলা; আর ছিল শরিকানী শক্তিপুজা। দুর্গাপুজা- কালীপূজা-জগদ্ধাত্রী পূজা হত। দশঘর জ্ঞাতির মধ্যে পূজো ছিল ছখানি দুর্গা, আটখানি কালী, চারখানি জগদ্ধাত্রী প্রতিমা গ’ড়ে পুজো হত, মাঝখানে একটি খড়ো আটচালা ঘিরে চারটি চণ্ডীমণ্ডপে। বিচিত্র ব্যবস্থা, কোন প্রতিমার সামনে বলি হত, কোন প্রতিমার পূজো হত বৈষ্ণব মতে। শালগ্রাম শিলা বিষ্ণুর প্রতীক, হিংসা রক্তপাত তাঁর সামনে নিষিদ্ধ, কিন্তু শ্যামনগরে ভটচাজবাড়ীতে শিলারূপী বিষ্ণুর সামনে তার নিষেধ ছিল না। কেবল সে কয়েকদিন তাঁর অন্নভোগ হত না। কারণ বলির খপরে রক্তপূর্ণ হলেই তখন সব অন্নব্যঞ্জন আমিষ হয়ে যায়। এছাড়া শিবমন্দিরে ছিল শিবলিঙ্গ।
শিষ্য-সেবক ছিল দেশ জুড়ে; কেউ চাইত বৈষ্ণব মন্ত্ৰ, কেউ শাক্ত, কেউ শৈব। শ্যাম- নগরের ভটচাজদের বাড়ীতে এসে যে যে-মন্ত্র চাইত তাই পেত। তাঁরা ছিলেন দেবতত্ত্বের ভাঁড়ারী। ভাঁড়ারে সব থাকত। যার যা প্রার্থনা, তার তাই মিলত। জমিদারেরা অধিকাংশ ছিলেন জগদ্ধাত্রীর উপাসক। বিশেষ ক’রে শাক্ত জমিদারেরা। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় জগদ্ধাত্রী পূজা করেছিলেন প্রথম। গোটা বাংলার হিন্দু সমাজের সমাজপতি, রাজ-ঐশ্বর্যে বাংলায় বিক্রমাদিত্য, নবরত্নের সভার মত সভা—তেমনি প্রতিষ্ঠা; লোকে বিশ্বাস করত জগদ্ধাত্রী পূজার ফল। তাই জমিদারদের বাড়ীতে জগদ্ধাত্রী মন্ত্র উপাসক ছিলেন বেশী।
রাণীভবানী ছিলেন, লোকে বলত, সাক্ষাৎ ভবানীর অংশোদ্ভূত। মহিমায় রাজরাজেশ্বরী, বুদ্ধিতে একটা সাম্রাজ্য চালাতে পারতেন। মীরজাফরেরা যখন ষড়যন্ত্র ক’রে ইংরেজদের সাহায্য নিয়ে নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে উচ্ছেদের মতলব করে তখন তাঁর কাছেও লোক পাঠিয়েছিল তারা। লোকে তাঁকে বলত অর্ধবঙ্গেশ্বরী। তাঁরা বিধবা মেয়ে পরমাসুন্দরী তারাকে বড়নগরে গঙ্গার ঘাটে দেখেছিলেন সিরাজউদ্দৌলা, গঙ্গার উপর নৌকা থেকে। দেখে পাগল হয়েছিলেন পাবার জন্যে। রাণীভবানী মেয়েকে কাশী পাঠিয়ে দিয়ে রক্ষা করেছিলেন তাকে। মীরজাফরেরা বিশ্বাস করেছিল, রাণী নিশ্চয় ষড়যন্ত্রে উৎসাহের সঙ্গে যোগ দিয়ে সাহায্য করবেন। কিন্তু তা তিনি করেন নি। তিনি যে কথাটা বলেছিলেন বাংলাদেশে সেটা প্রবাদবাক্য হয়ে গেছে। আজও লোকে বলে—খাল কেটে কুমীর এনো না। রাণীভবানীর পোষ্যপুত্র রামকৃষ্ণ রায় পঞ্চমুণ্ডীর আসনে বসে কালীসাধনা করতেন। আজও বড়নগরে সে পঞ্চমুণ্ডীর আসন আছে। রাণী বাংলাদেশে নাকি এক লক্ষ কালী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন—গ্রামে নগরে, তার জন্য নিষ্কর জমি দিয়েছিলেন। সে পূজা সে নিষ্করের উপর আজও চলে। রামকৃষ্ণ রায়, মহারাজা রামকৃষ্ণ রায়, সুলতা, যেখানে শবাসনে বসতেন তার সামনেই আজও আছে গোপাল মন্দির। রাণীভবানীর কন্যা তারা দেবীর প্রতিষ্ঠিত গোপাল। সেকালের বাংলাদেশে শক্তিমন্দিরের পাশে সব বাড়ীতেই নারায়ণ সেবা যুগলবিগ্রহ সেবা আছে। সুতরাং গুরুগিরি যাদের পেশা তাদের ঘরে পূজার এ বিচিত্র প্রথা থাকবে, তাতে আশ্চর্য কি সুলতা!
সুলতা হাতের চায়ের কাপটা ট্রের উপর নামিয়ে দিয়ে বললে—পড়েছি কিছু কিছু। শুনেছিও। কিন্তু এমন অর্থহীন ব্যাপার—যার মাথামুণ্ডু নেই, এটা জানতাম না!
সুরেশ্বর হেসে বললে—মাথা থেকে হাত, পা, আঙুল—সবই তাঁরা হয়তো বেঁচে থাকলে দেখিয়ে বুঝিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু সে আমি পারব না। তবে এইটুকু বলতে পারি যে, এর ভিতর থেকেও শুদ্ধাচারী পরিচ্ছন্ন মানুষের অভাব ছিল না। আজও তাকিয়ে দেখ সুলতা, দুনিয়ার দিকে, ধনতন্ত্র, সমাজতন্ত্র পাশাপাশি বাস করছে, এ বলছে ওর মধ্যে নোংরামি বেশী, এ বলছি ওর ভিতরের কদর্যতার মত কদর্যতা আর হয় না-নেই। ও ঝগড়া থাক। আমি বলছে সেকালের মানে ১৮১৫ সালের কথা। সেই কথাই বলি।
১৮১৫।১৬ সালে এরপর শ্যামাকান্ত একদিন নিরুদ্দেশ হলেন—স্ত্রী শিশুপুত্র সব ফেলে। এঁরা ভেবেছিলেন—গেছে, আবার ফিরবে দু’তিন মাস পর। শ্যামাকান্ত যেতেন তো মধ্যে মধ্যে গান শোনাতে। কিন্তু না, ফিরলেন না!
শ্যামাকান্ত বেরিয়েছিলেন পূর্ণ সন্ন্যাস নিয়ে। তান্ত্রিক সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়েছিলেন—সিদ্ধি তাঁকে পেতেই হবে।
সন্ন্যাসের নিয়ম হল—সব ত্যাগ করতে হয়—নাম পরিচয় জাতি বর্ণ–ব্রাহ্মণ হলে উপবীত এবং বলতে হয়, ইহলোক এমন কি পরলোক পর্যন্ত ত্যাগ ক’রে তবে সন্ন্যাস নিতে হয়। কিন্তু শ্যামাকান্ত তাঁর তানপুরার মমতাটি ছাড়তে পারেন নি, সেটিকে ঘাড়ে ক’রে বেরিয়েছিলেন।
এসে উঠেছিলেন কালীঘাটে। মহাপীঠ–কালীতীর্থ কালীঘাট। পাশে কেওড়াতলার মহাশ্মশান; সেখানে সাধনা করবেন, শব-সাধনা। কালীঘাটে এসে দিনকয়েকের মধ্যে তাঁর খাতির জমে উঠেছিল—সন্ন্যাসী হিসেবে নয়, গায়ক হিসেবে। কেওড়াতলার শ্মশান তখন সত্যই মহাশ্মশান। ১৮১৬ সাল। তখন সুন্দরবনের আভাস কলকাতার ময়দান থেকেই শুরু। মধ্যে মধ্যে বাঘের উপদ্রব হয় আশেপাশে। মধ্যে মধ্যে ডাক শোনা যায় রাত্রে। তারই মধ্যে নিশাচরের মত ঘুরে বেড়াতেন। রাত্রে জপ করতেন। শবের সন্ধান করতেন। একদিন পেলেন এক শব জোয়ারে গঙ্গার জলে ভেসে যাচ্ছিল। শ্যামাকান্ত স্নান করছিলেন। দেখতে পেলেন জোয়ারে ভেসে যাচ্ছে একরাশি কালো চুল আর ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভেসে উঠছে একটি যুবতী নারীদেহ। তিনি ঝাঁপ দিয়ে পড়ে সাঁতরে গিয়ে ধরলেন সেই দেহ। এবং তুলে নিয়ে এলেন। তখন শীতকাল। মকর সংক্রান্তিতে গঙ্গাসাগর সঙ্গমে স্নানের জন্য সাধু-সন্ন্যাসীর ভিড় জমেছে। তিনি সেই দেহ টেনে এনে লুকিয়ে রাখলেন সযত্নে। তিথিও নাকি অভীষ্ট তিথি ছিল। সেই রাত্রে তিনি, শ্মশানের নিবিড়তম অভ্যন্তরে তাঁর যে আসন ছিল, সেইখানে শবাসনে বসেছিলেন। কিন্তু সিদ্ধি তাঁর হয়নি। হয়েছিল উল্টো। সঠিক কি ঘটেছিল তিনি জানেন। তবে লোকে বলত—তাঁকে আসন-ওই শবের বুক থেকে মহাশক্তি ছুঁড়ে পেলে দিয়েছিলেন গঙ্গার কিনারায়। তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিলেন সমস্ত রাত্রি। তন্ত্রসাধনায় এই ধরনের ঘটনার কথা অজস্র শোনা যায়; তুমি শুনেছ কিনা জানি না। নাটোরের রাজা রামকৃষ্ণ রায় সম্পর্কে এমনি গল্প আছে। তিনি শবাসনে বসে যখন ধ্যান করছেন, তখন নাকি মা রাণীভবানীর কণ্ঠস্বরে চমকে উঠে দেখেছিলেন—তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে শাস্তি দিতে আসছেন। অথচ রাণীভবানী তখন ঘরে নিদ্রামগ্ন। রাজা রামকৃষ্ণ এই মায়াময়ী রাণী ভবানীর ভয়ে আসন ছেড়ে উঠে পালাতে গিয়ে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন। এমনি কিছু ঘটেছিল শ্যামাকান্তের। তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন। পরদিন সকালে তাঁকে দেখতে পেয়েছিলেন আর এক সন্ন্যাসী। উত্তর প্রদেশের বৈষ্ণব সাধু। শুনেছি মাঁকি শবাসনের শবটি তখন ছিল না। ছিল একটা কঙ্কাল আর একরাশ চুল।
ওই বৈষ্ণব সন্ন্যাসীর যত্নেই শ্যামাকান্ত বেঁচেছিলেন। সুস্থ হতে কিছুদিন লেগেছিল।
শ্যামাকান্ত মৃত্যুকালে বলেছিলেন-ওঃ-তার সঙ্গে যদি দেখা না হত! ওই তার ছবি সুলতা। ওই দেখ মৃত্যুশয্যায় শ্যামাকান্ত! মুখের রেখায় রেখায় আলোর ছটা পড়েছে। এ পাশে বীরেশ্বর রায়, ওপাশে ভবানী দেবী, পায়ের তলায় বিমলাকান্ত।
—তিনি মারা গিয়েছিলেন যে বছর বীরেশ্বর রায় ভবানী দেবীকে ফিরে পান সেই বছর—১৮৬০ সালে। এখানকার লোকে জানত তিনি মারা গিয়েছিলেন চল্লিশ বছর আগে এই কীর্তিহাটেই কাঁসাইয়ের জলে ডুবে। কিন্তু না। তিনি জলে ভেসে গিয়ে কাঁসাইয়ের একটা বাঁকে গিয়ে চড়ায় উঠেছিলেন। চল্লিশ বছর পরে হতভাগ্য শ্যামাকান্ত মৃত্যুর সামান্য কিছুদিন পূর্বে সুস্থ হয়েছিলেন। তাঁর সেই উন্মাদরোগ বল উন্মাদরোগ, অথবা মহাশক্তির নিষ্ঠুর প্রহার বল নিষ্ঠুর প্রহার থেকে মুক্তি পেয়ে বীরেশ্বর রায়কে পত্র লিখেছিলেন সাক্ষাৎ প্রার্থনা করে। সে পত্রে তিনি তাঁর জীবনের বিচিত্র ঘটনাগুলি অকপটে খুলে লিখে অনুরোধ করে- ছিলেন—“একবার তোমার সাক্ষাৎ প্রার্থনা করি। তুমি আমার জামাতা—আমার যে পরম পুণ্যফলকে, মহামায়ার প্রসাদকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়া বিনষ্ট করিতে চাহিয়াছিলাম তাহা তুমি উদ্ধার করিয়াছ। আমি যাহা বলিতে চাহিয়াও বলিতে পারি নাই, মহাকোপে কুপিতা শক্তি যাহার জন্য আমার কণ্ঠরোধ করিয়া গলা টিপিয়া ধরিয়াছে, সেই কথা তুমিই আমাকে বলাইয়াছ। তাহা অবশ্য স্পষ্ট হয় নাই। পরে মহাসিদ্ধ সাধকের কৃপায় তাহা আমি বলিয়া আজ সুস্থ হইয়াছি। আজ আমি জাতিভ্রষ্ট, সাধনাভ্রষ্ট, আমি ঘৃণিত—হয়তো মৃত্যুতে অনন্ত নরক। এ সময়ে তোমার একবার সাক্ষাৎ প্রার্থনা করি।”
বীরেশ্বর রায় গিয়েছিলেন। মৃত্যুকালে শান্তিতে মরেছিলেন শ্যামাকান্ত।
তাঁর সে পত্র আমি পেয়েছি। আমার কাছে আছে। এইখানেই আছে। আরও একখানি পত্র; সে পত্র লিখেছিলেন—কীর্তিহাটের কুড়ারাম রায় ভট্টাচার্যের কুলগুরুর বংশধর, সোমেশ্বর রায়ের কুলপুরোহিত কালীমায়ের সেবক, সোমেশ্বর রায়ের দেবোত্তরের অন্যতম ট্রাস্টি রামব্রহ্ম ন্যায়রত্ন। তিনি পদত্যাগ করবার জন্য বীরেশ্বর রায়কে পত্র লিখেছিলেন। সব কথা তিনি মুখে মুখে বলতে পারেন নি-বীরেশ্বর রায়কে পত্র লিখে জানিয়েছিলেন।
বীরেশ্বর রায় তখন কীর্তিহাটে স্থায়ীভাবে বাস করছেন। এসেছেন ওই মিউটিনির সময়। ১৮৫৭ সালের জুন মাসে কলকাতার অবস্থা দেখে চলে এসেছেন। মেটিয়াবুরুজে বন্দী অযোধ্যার নবাব ওয়াজিদ আমি শাকে যেদিন ফোর্ট উইলিয়মে নিয়ে গিয়ে আটক করে ইংরেজ কর্নেল, সেদিন ওয়াজিদ আলি শা কেঁদেছিলেন। সেই দৃশ্য দেখার পর বেদনায় হোক, ভয়ে হোক, হয়তো বা দুয়ের জন্যই কীর্তিহাটে ফিরে এসে বিষয় নিয়ে প্রমত্ত হয়েছিলেন।
ডিসেম্বর মাসে একবার কলকাতায় গিয়েছিলেন, একটা সই দেবার জন্যে। রাইট অনারেবল চার্লস জন ভাইকাউন্ট ক্যানিং-এর কাছে বাঙালী মহারাজা রাজা এবং জমিদারের পক্ষ থেকে, বিদ্রোহী সিপাহীদের হাত থেকে দিল্লী উদ্ধার করার পর, অভিনন্দন এবং আনুগত্য জানিয়ে যে Address দেওয়া হয়েছিল, তাতে সই করতে গিয়েছিলেন।
My Lord—We the Rajas, Zeminders, Talookdars, Merchants and other Natives of the Province of Bengal, take the earliest opportunity, on retaking Delhi, to offer your Lordship in Council our warmest congratulations on the signal success which has attended the British arms, under the circumstances unparalled in the annals of British India—
এ দরখাস্তে প্রথম সই ছিল—মহারাজাধিরাজ মহাতাব চান্দ বাহাদুর বর্ধমানাধিপতির। দ্বিতীয় সই ছিল রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের। বীরেশ্বর রায়ের সই তার বেশী নিচে ছিল না। আড়াই হাজার সই ছিল এ দরখাস্তে।
সই যাঁরা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রাচীন আমলের জমিদার রাজা যাঁরা তাঁরা অনেকে মনের ভাব চেপে দরখাস্ত করেছিলেন হয়তো, কিন্তু বীরেশ্বর রায় মনোভাব চাপেন নি। কুড়ারাম রায় কোম্পানীর কর্মচারী থেকে জমিদার। তাঁর সই অকপট। তাঁর পরিচয় চিঠিপত্রে আছে। এরপর নিশ্চিন্ত হয়ে ইংরেজের ছায়াপত্রতলে থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে তিনি আপন পরিকল্পনা মত দেশের উন্নতি, তাঁর জমিদারীর উন্নতি করতে আরম্ভ করেছিলেন। দুষ্টকে দমন—শিষ্টকে পালন করে আদর্শ জমিদার হতে চেয়েছিলেন।
স্কুলের পত্তন হয়েছিল। কাঁসাইয়ের ধার বরাবর বন্যারোধী বাঁধের ভাঙনগুলিকে সংস্কার করিয়েছিলেন। গ্রামের রাস্তাঘাট মেরামত করিয়েছিলেন।
ওদিকে শুরু হয়েছিল নুতন পত্তনী নেওয়া মহলগুলিতে নুতন বন্দোবস্ত। খাজনাবৃদ্ধি, পতিত আবাদ, সেচের জন্য বাঁধ তৈরী, পুকুর কাটাই। ভাদ্র-আশ্বিনে গরীব প্রজাদের ধান চাল সাহায্য। এবং তার সঙ্গে বিচার।
তার সঙ্গে গিরীন্দ্র আচার্যের অধীনে একটি বড়রকমের মামলা সেরেস্তা খুলেছিলেন। প্রথম মামলা দায়ের হয়েছিল গোপাল সিংয়ের নামে। একসঙ্গে আঠারটি মকদ্দমা। গোটা জমিদারীতে প্রথম বছরেই দেওয়ানী ফৌজদারীতে চারশো মামলা দায়ের হয়েছিল মেদিনীপুর আদালতে।
দ্বিতীয় বছরে মামলার সংখ্যা বাড়ল। এবার মামলা বাধল শ্যামনগরে। শ্যামনগর বীরেশ্বর রায় পত্তনী নিলেন—ওই দে সরকারদের কাছ থেকে। শ্যামনগরের প্রজাদের মুখপাত্র দাঁড়ালেন—কমলাকান্ত ভট্টাচার্য।
কমলাকান্ত তখনও রত্নেশ্বর রায় নন, তখনও তাঁর পরিচয়-তিনি বীরেশ্বর রায়ের ভাগ্নে। কমলাকান্তের পিছনের প্রজার দলের মধ্যে সর্বাগ্রে ছিলেন—ঠাকুরদাস পাল।
সুরেশ্বর উঠে গিয়ে ওদিকের টেবিল থেকে একটা কাগজের বান্ডিল নিয়ে এসে বসল। বললে—লাট যুগলপুরের পত্তনী পাট্টার দলিলখানা আর ওই বিষয়ের চিঠিপত্রে বিচিত্র কথা আছে। শোনাব তোমাকে। ১৮৫৯ সাল। বাংলাদেশে সিপাহী বিদ্রোহের আগুন নিভেছে। কোম্পানীর হাত থেকে ভারতবর্ষ ইংলন্ডেশ্বরীর এম্পায়ার অথবা খাসমহল হয়েছে। বৃটিশ এম্পায়ার এস্টাবলিশড বাই ল’ এই তার বয়ান। জমিদারেরা পারমানেন্ট সেটেলমেন্টের আইনবলে জমিদারীর ঊর্ধ্ব-অর্ধের মালিক। কিন্তু ইংলন্ডেশ্বরীর ইংলন্ডজাত প্রজাদের রাইট কালাআদমীর চেয়ে অনেক বেশী। তারা তখন এদেশে ব্যবসা খুলে বসেছে একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্ত পর্যন্ত। সে সময় নীলের কুঠীর সাহেবদের দাপট উঠল চরমে। নীলবিদ্রোহ বাঙলার ইতিহাসের একটা অধ্যায়। এখান থেকেই নতুন যুগের আন্দোলনের শুরু।
জন রবিনসন বীরেশ্বর রায়ের বন্ধু ছিল। ছেলেবেলায় সে এই সময় শ্যামনগরে কুঠীর পত্তন করেছিল। শ্যামনগরের জমিদার দে-সরকারেরা জন সাহেবের কুঠীতে টাকা লগ্নী করে রবিনসন সাহেবের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল। দে সরকাররা যুগলপুরের ব্রাহ্মণ, সঙ্কোপ, কায়স্থ প্রজাদের বিদ্রোহের জন্য করেছিলেন এটা। ব্রাহ্মণ প্রজা বড় খারাপ সুলতা, তার মানে ইন্টেলেকচুয়েল বলতে পার।
দে-সরকারদের কর্তা ছিলেন প্রথমে মহাজন, চড়া সুদে টাকা ধার দিতেন। লাট যুগলপুর —খানচারেক মৌজা, তার অন্তর্গত শ্যামনগর-রাধানগর; এই দুখানি গ্রামই বড়। রাধা ও শ্যাম নামাঙ্কিত দুখানি তৌজির জন্যই নাম যুগলপুর। এ ছাড়া দুটি চক—দুখানি। একখানিতে ষোল আনা মুসলমানের বসতি, নাম চক ঠাকুরপাড়া। অন্যখানির নাম চক পাকপাড়া বা পাইকপাড়া, এখানকার বাসিন্দাদের মধ্যে মুসলমান, বাগ্দী, বীরবংশী ও বাউড়ীদের মিলিয়ে বাস। লাট যুগলপুরের ইতিহাস একটু বিচিত্র। সে ইতিহাস না বললে সবটা পরিষ্কার হবে না। একমাত্র মুসলমান সম্প্রদায়ের গ্রাম ঠাকুরপাড়ার মিঞারাই এখানকার তালুকদার ছিলেন। ঠাকুরপাড়ার মিঞারা মুসলমান হলেও উপাধি ছিল ঠাকুর। তার কারণ, বীরেশ্বর রায়ের আমলের একশো বছর পুর্বেও এই ঠাকুরেরা ছিলেন ব্রাহ্মণ। প্রসিদ্ধ যোগীর বংশ ছিল ঠাকুর বংশ। যোগযাগ অনেক কিছু ছিল এই বংশে। মাননীয় ব্রাহ্মণ বংশ।
সতেরশো একচল্লিশ-বিয়াল্লিশ সালে বর্গীরা যখন বাংলাদেশে প্রথম পঙ্গপালের মত এল, যখন কুড়ারাম ভটচাজ দশ-এগার বছরের ছেলে, মায়ের হাত ধরে ঘর থেকে বেরিয়ে পথে পথে পালিয়েছিলেন, সেই সময় এই ঠাকুর বংশের প্রধানজন ত্রিভুবন ঠাকুর নসীব গুণে ঠিক ঠিক বলে দিয়েছিলেন; বলে দিয়েছিলেন, পথে এই বিপদ হবে, বিপদ থেকে নবাব রক্ষা পাবেন এবং শেষ পর্যন্ত জিতবেন। ভাস্কর পণ্ডিত আর ফিরবে না, এ কথাটি পর্যন্ত ছিল তার ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে। সমস্ত অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেলে নবাব সন্তুষ্ট হয়ে এই লাট যুগলপুর তাঁকে দিয়েছিলেন সামান্য একশো তঙ্কা রাজস্বের বিনিময়ে। এবং নিজের গায়ের বহুমূল্য শাল খুলে তাঁকে পরিয়ে দিয়েছিলেন। সেই শাল গায়ে দিয়ে গ্রামে ফিরলে বংশের নবীনেরা কথাটা গৌরব করে বলে বেড়িয়েছিলেন। তখন ত্রিভুবন ঠাকুর শুধু ঠাকুর, লাট যুগলপুরের জমিদার। কিন্তু যুগলপুরের যশমানধারী ব্রাহ্মণেরা এ অনাচার সইতে পারেন নি। তাঁরা বলেছিলেন- নবাবের গায়ের শাল, ও শাল গায়ে তিনি মুসলমানী খাদ্য খেয়েছেন, হাত না ধুয়ে রুমালে হাত মুছে সেই হাত ওই শালে ঠেকিয়েছেন। ত্রিভুবন ঠাকুর যখন সেই শাল গায়ে দিয়েছেন, তখন তাঁর হাত শালে ঠেকেছে, সেই হাত মুখে ঠেকেছে, সুতরাং তাঁর জাত গেছে। কলমা না পড়েও তিনি মুসলমান হয়ে গেছেন।
ত্রিভুবন ঠাকুরদের যোগসিদ্ধির জন্য খাতির ছিল অসাধারণ। শ্যামনগরের ব্রাহ্মণদের রাগ ছিল তাঁদের উপর, রাধানগরের কায়স্থদেরও রাগ ছিল—তার কারণ ঠাকুরেরা কায়স্থদের শুদ্র বলে তাঁদের কোন দান নিতেন না তাঁদের মন্ত্র দিতেন না। তাঁরা ছিলেন ব্রাহ্মণদেরও পূজনীয়। তাঁদের প্রতি এঁদের অবজ্ঞাও ছিল। সুতরাং এই নবাবী শাল দান নেওয়ার ত্রুটির সুযোগ তাঁরা ছাড়লেন না। তাঁরা ব্রাহ্মণ সমাজের পঞ্চজন এবং রাধানগরের কায়স্থ সমাজ তাঁকে পতিত করে প্রতিশোধ নিলেন। ত্রিভুবন ঠাকুর কিন্তু টললেন না। বললেন—যিনি দেশের অধিপতি, তিনি জাতির ঊর্ধ্বে। শাস্ত্রে বলে, ‘সর্বদেবোময়ো রাজা’, তিনি তাঁর গলা থেকে মুক্তার মালা কি স্বর্ণহার খুলে দিলে তা গ্রহণ করতে আছে, আর শাল গ্রহণেই দোষ?
এ পক্ষ বলেছিল—স্বর্ণ রৌপ্য মণিমুক্তা কখনও অশুদ্ধ হয় না। উচ্ছিষ্ট স্পর্শেও না। শাস্ত্রে আছে, বিষ্ঠাতে স্বর্ণ খণ্ড পড়ে থাকলে তাকে লক্ষ্মীর প্রসাদ বলে তুলে নিতে হয়। ধুলে শুদ্ধ। শাল বস্তু সে পশম রেশম-কার্পাস যাই হোক।
ত্রিভুবন ঠাকুর প্রশ্ন করেছিলেন—পদ্মনাভ ভট্টাচার্যের পিতামহ জনার্দন ভট্টাচার্যকে। জনার্দন ভট্টাচার্য বন্ধু ছিলেন তাঁর। গোপনে সাধন-ভজনের তত্ত্ব আলোচনা করতেন তাঁরা।
জনার্দন ভট্টাচার্য চুপ করেই ছিলেন। তাঁর অন্তরের কথা তিনিই জানেন, তবে স্বপক্ষে- বিপক্ষে কোন কথাই বলেন নি।
ত্রিভুবন ঠাকুর প্রশ্ন করেছিলেন—জনার্দন, তুমি কি বল? তোমার মত?
জনার্দন বলেছিলেন—আমি তো দেশের বাইরে নয় ত্রিভুবন। কি বলব?
ত্রিভুবন আর কোন কথা বলেন নি। চলে এসেছিলেন নিজের ঠাকুরপাড়ায়। এবং কয়েকদিনের মধ্যেই মেদিনীপুরের ফৌজদারকে সংবাদ দিয়েছিলেন যে, তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবেন। মেদিনীপুর থেকে মোল্লা মৌলভী এবং কিছু সিপাহী আনিয়ে বাড়ীতেই কলমা পড়েছিলেন।
তার আগে বাড়ীর বিগ্রহ এবং শিলা যা ছিল সব বিসর্জন দিয়েছিলেন গঙ্গার গর্ভে। ভেঙে অঙ্গহীন করতে বোধহয় পেরে ওঠেন নি। এবং ঠাকুরপাড়ার জ্ঞাতিবর্গ যারা তাদের বলেছিলেন-যারা কলমা পড়তে রাজী আছে তারা থাক এ পাড়ায়। যারা রাজী নও, তারা অন্ততঃ এ পাড়া ছেড়ে অন্যত্র যাও। শ্যামনগর-রাধানগর যদি যাও তবে ভূমি আমি নিষ্কর দেব। কিন্তু এ পাড়ায় বাস, সে তোমাদেরও সুবিধে হবে না। আমারও না। যারা কলমা পড়বে, আমার সঙ্গে থাকবে, তাদের আমি প্রত্যেককে কুড়ি বিঘা নানকার দেব। তাদের ছেলে-পুলেদের নবাব সরকারে চাকরির ব্যবস্থা করে দেব। তোমরা বুঝে দেখ! তবে এটা মনে রেখ, পতিত তোমরাও আমার সঙ্গে হয়েছ। নবাব দরবার থেকে ফিরে এসেই তোমাদের সকলের বাড়িতে আমি মুরশিদাবাদের মিষ্টান্ন পাঠিয়েছি। তোমরা খেয়েছ।
কেবল দু’ ঘর ছাড়া সকলে ত্রিভুবন ঠাকুরের সঙ্গেই থেকেছিল, তাঁকে ছাড়তে তারা চায়নি। দু’ ঘর চলে গিয়েছিল স্থানান্তরে। শ্যামনগর-রাধানগরেও তারা থাকে নি।
ত্রিভুবন ঠাকুর কলমা পড়ে মুসলমান হয়ে নাম নিয়েছিলেন মহম্মদ আবুসবের খাঁ। কিন্তু খাঁ উপাধি তাঁর কায়েম হয় নি, লোকে তাঁকে ঠাকুরই বলত। আবু ঠাকুর!
আবু ঠাকুর মসজিদ করেছিলেন মন্দির ভেঙে। মুরশিদাবাদ থেকে কারিগর রাজমিস্ত্রী এসেছিল। স্বয়ং নবাব পাঠিয়েছিলেন। মসজিদের পর হয়েছিল তাঁর পাকা দালানবাড়ী। ঠাকুর সাহেবের হাবেলী। হাতী কিনেছিলেন, ঘোড়া কিনেছিলেন। আর ওই ছিটমহল ঠাকুরপাড়ার একটু দূরে ওরই ভিতরে মুসলমান এবং ডোম বাগ্দী পাইকদের এনে বাস করিয়েছিলেন। নাম দিয়েছিলেন চক পাইকপাড়া।
ঠাকুর মিঞা কলমা পড়ে মুসলমান হয়েছিলেন, দেব-বিগ্রহ গঙ্গায় বিসর্জন দিয়েছিলেন এবং ব্রাহ্মণ শাস্ত্রজীবী থেকে জমিদার হয়েছিলেন। কিন্তু যে বিদ্যা তিনি আয়ত্ত করেছিলেন, যোগবিদ্যা আর অদৃষ্ট গণনাবিদ্যা সে তাঁর কোথায় যাবে। তা যায়ও নি এবং তিনি তাঁর চর্চাও ছাড়েন নি। আরও একটি নিয়ম তিনি করেছিলেন—কোরবানীতে তিনি দুম্বা খাসী ছাড়া গরু কোরবানী করেন নি।
তিন পুরুষ পর্যন্ত ঠাকুরবংশ অপ্রতিহত প্রতাপে জমিদারী করেছিলেন, মীরকাশেম আলি খাঁর সময় পর্যন্ত।
শ্যামনগর-রাধানগরের ব্রাহ্মণ কায়স্থ সদগোপদের সঙ্গে ঠাকুরবংশের লড়াই চলেছে বিচিত্র পথে। ঠাকুর মিঞা বা আবু ঠাকুর তাদের উপর জমিদারী করে গেছেন সেলাম নিয়ে, খাজনা নিয়ে। বাস আর কিছু না। শুধু সেলাম আর টাকা। কারুর ধর্মে তিনি হাত দেন নি। কারুর কন্যাকে বংশে কারুর সঙ্গে বিয়ে দেবার জন্যে জেদ করেন নি। বিয়ে-সাদী ঠাকুরপাড়ার জ্ঞাতিদের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। আর বিয়ে-সাদী যা দিয়েছেন তা বেছে বেছে হাজী, যাঁরা হজ করে এসেছেন, তাঁদের বাড়ীতে। একটা পরিবার। ত্রিভুবন ঠাকুরের দুই বিবাহ, তাতে পুত্র তিনটি, কন্যা তিনটি, জ্ঞাতি দশ-বারো ঘর, সুতরাং বিয়ে-সাদীর জন্যে বাইরে যেতে হয় নি।
আবু ঠাকুর সকালে দলিজায় বসতেন, জমিদারী করতেন, নালিশ শুনতেন, বিচার করতেন। ব্রাহ্মণ কায়স্থ যারা আসত, তাদের জন্যে আলাদা ফরাস থাকত এবং তা থাকত তাঁর বা ঠাকুর মিঞাদের আসন থেকে নিচে। এসে সেলাম দিতে হত, যাবার সময় সেলাম দিয়ে যেতে হত। জরিমানা করতেন, সে জরিমানার মাফ ছিল না। শ্যামনগর-রাধানগরে খাজনা বাড়িয়েছিলেন, বিঘাপ্রতি দেড় টাকা হতে দু টাকা আড়াই টাকায়। লাট যুগলপুরের দুই তৌজি শ্যামনগর-রাধানগরের বাৎসরিক ডৌল জমা ছিল পাঁচ হাজার টাকা, তিনি তাকে বাড়িয়ে করেছিলেন, সাড়ে সাত হাজার। খাজনা এক পয়সা বাকী থাকত না। তিনি নায়েব-গোমস্তা রেখেছিলেন ওই রাধানগরের কায়স্থদের। ওদেরই মধ্যে কয়েকজনকে মহাজনীতে সাহায্য করে প্রজার কাছে খাজনা আদায় করতেন। টাকাও তিনি তাদের দিতেন বিনা সুদে। তারা প্রজার খাজনা আদায়ের সময় কাছারীতে প্রজার হয়ে খাজনার টাকা সেরেস্তায় দিত এবং সুদসুদ্ধ আদায় করত। তিনি মুসলমান, তিনি সুদ নিতেন না। মোট কথা তিনি বিচিত্র উপায়ে দুই তৌজির হিন্দু প্রজাদের জব্দ করেছিলেন নিঃস্ব করে। ব্রাহ্মণেরা কেউ সংস্কৃতে তাঁর স্তব করে সংস্কৃতে শ্লোক তৈরী করলে, শ্লোকপিছু পাঁচ টাকা ইনাম দিতেন। এবং দরকার মত সংশোধন করে দিতেন।
কিন্তু শ্যামনগরের কোন ব্রাহ্মণ তাঁর স্তব রচনা করে নি।
তাঁর অন্তে তাঁর ছেলে গুলমহম্মদ ঠাকুর নাকি সিদ্ধযোগী ছিলেন। তিনি অত্যন্ত উদার ছিলেন। হজ করে এসেছিলেন তিনি। তিনিও যোগ করতেন। এমন বাক্সিদ্ধ ছিলেন যে যা বলতেন তাই ঘটত।
তৃতীয় পুরুষে এই যুগলপুর নিয়ে গোলমাল লাগল কোম্পানীর সঙ্গে। তৃতীয় পুরুষে তখন তিন ছেলে, দুই মেয়ে, এক ছেলে ভোগী, এক ছেলে পূর্বপুরুষের মত যোগী, ছোট ছেলে নবাবী পল্টনে ঢুকেছিল; পলাশীর যুদ্ধে নবাবের হয়ে লড়তে গিয়ে মরেছিল। বড়জন ভোগবিলাসের জন্য প্রথম গিয়ে বাস করেছিলেন মুরশিদাবাদে। তারপর গিয়েছিলেন নবাব কাসেম আলী খাঁর সঙ্গে মুঙ্গের। সেখানেই থেকে গেছেন। ফেরেন নি। সম্পত্তি নিয়ে আছেন যিনি, যোগী এবং জমিদার, তিনি মেঝলা ঠাকুর মিঞা। এদিকে সরকার তখন কোম্পানীর হাতে গিয়েছে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী যুগলপুর লাটের তালুকদারের উপর নোটিশ জারী করলেন—কোম্পানীর নতুন আইন অনুযায়ী তোমার জমিদারী তুমি নতুন করে বন্দোবস্ত নাও। শুধু নতুন করেই নয়, নতুন নিয়মে বৎসর ডাক অনুযায়ী বন্দোবস্ত নিতে হবে তোমাকে।
মেঝলা ঠাকুর মিঞা নোটিশ ফেলে দিয়ে ‘বললেন—ফিরিঙ্গী লোক বলে কি? আরে ঠাকুরবংশের জমিদারী ফরমান খুদ আলীবর্দী খাঁ বাহাদুরের। তাকে নাকচ করবে কে? বলে দিলেন—এ কভি না হো সকতা হ্যায়। দিল্লগী হ্যায় ইয়ে!
মেঝলা ঠাকুর মিয়া একদিকে আমীর, অন্যদিকে ফকীর, লোকে জানত তাঁদের বংশের গুপ্তবিদ্যা হঠযোগ, যার চর্চা করে বাপ গুলমহম্মদ নানান বিচিত্র কাজ করতেন, বাকসিদ্ধ হয়েছিলেন, তাই তিনি বাপের কাছ থেকে নিয়ে তার চর্চা করেন। কোন নেশা করেন না, অথচ সর্বদাই ঢুলু ঢুলু চোখে চেয়ে থাকেন। শখ ছিল শুধু পান খাওয়ার। মুক্তার চুন দিয়ে পান খেতেন, তার সঙ্গে এমন মশলা থাকত যা খেয়ে শীতের দিনেও মখমলের পাঞ্জাবি পরে ঘামতেন। নোকরকে পাখার হাওয়া দিতে হত। ভাষা ছিল মিষ্ট। কিন্তু এতটুকু অমর্যাদা বোধ করলে সাপের মত মুহূর্তে ফোঁস করে ফণা তুলতেন। যুগলপুরের ব্রাহ্মণদের উপর রাগ তাঁরও ছিল।
সেই ত্রিভুবন ঠাকুর বা আবু ঠাকুরের প্রাপ্য সেলামী-সেলাম আদায় করতে নিত্য একবার হাতী চড়ে গ্রামে ঘুরতেন।
শখ ছিল গান-বাজনায়। কিন্তু মেয়েদের গলায় ঠুংরী-টপ্পার রুচি ছিল না, রুচি ছিল ধ্রুপদে। খেয়ালও ভালবাসতেন। নিজে ছিলেন বড় পাখোয়াজী।
কোম্পানীর সঙ্গে এই নিয়ে তিনি লড়াই করেছিলেন সাত-আট বছর। ঠিক এমনি মামলা তখন কাশীজোড়ার রাজার সঙ্গে হয়ে গেছে কোম্পানীর। কোম্পানী সুপ্রীম কোর্টে হেরেছিল। কিন্তু হেস্টিংস সাহেব ছিল ধুরন্ধর লোক। সে ইম্পে সাহেবকে ঘুষ দিয়ে ইজ্জত রক্ষা করেছিল। এরপর আইনও পাস করেছিল, জমিদারী কেড়ে নিয়ে বন্দোবস্তের জন্যে।
কুড়ারাম রায় ভটচাজ তখন গঙ্গাগোবিন্দের সঙ্গে বাংলার জমিদারী নাটকের প্রথম অঙ্কে একটি পার্শ্বচরিত্র। কিন্তু তাঁর হাত অনেক। কুড়ারাম রায়ের ব্যবস্থায় জমিদারী বেঁচে গিয়েছিল ঠাকুরদের। কিন্তু আদায় কোম্পানীর খাসে চলে গিয়েছিল। আদায় করে রেভেন্যু কেটে নিয়ে বাকী টাকা আসত মেঝলা ঠাকুরের হাতে। কোম্পানী পাঠাতেন।
একশো টাকা রেভেন্যু তখন সাড়ে সাতশো টাকা, আর সরঞ্জামী আদায় খরচ শতকরা পাঁচ টাকা বাদ যেত। ঠাকুর মিঞার নায়েব ছিল রাধানগরের মাধব দে সরকার। মাধব দে সরকার ঠাকুর মিঞাদেরই অনুগৃহীত মহাজন হিসেবে কাজ করত। ঠাকুর তালুকদারীর সব তার নখদর্পণে। এবং তার টাকাও ছিল। কোম্পানীর টাকা যুগিয়ে সে ঠাকুরের টাকা যুগিয়ে যেত।
গোল বাধল ১৭৯৩ সালে। পারমানেন্ট সেটেলমেন্টের সময়। কোম্পানি যখন দশশালা বন্দোবস্তের জন্য জরীপ করে আদায়ের উপর শতকরা নব্বুই টাকা জমা ধার্য করবেন বলে জমিদারদের উপর ফতোয়া ফরমান জারী করলেন, তখন ঠাকুর বললেন-তোবা তোবা। এ কি বাত! এ হয়, না হতে পারে? নবাবী পাঞ্জা শীলমোহর দস্তখত দেওয়া বন্দোবস্তী বাতিল? নয়া বন্দোবস্ত নিতে হবে ফিরিঙ্গী বানিয়ার কাছে? হায় আল্লা রসুল! হায় পয়গম্বর! নেহি, এ কভি না হো সকতা হ্যায়। এ কাম যদি আমি করি তবে সে হবে গুনাহগারী। জমিদারী যানে দেও। ঠাকুরবংশ একসঙ্গে জমিদার বটে, আবার ফকীরও বটে। যোগীর বংশ
কেউ রাজী করাতে পারে নি। বাড়ীতে মেয়েরা কেঁদেছিল। ঠাকুরপাড়ার জ্ঞাতিরা দরবার করেছিল, কিন্তু মেঝলা ঠাকুর নড়েন নি!
তাঁর এক-কথা-এ কভি না হো সক্তা হ্যায়।
বাদশা দেওয়ানী দিলে ফিরিঙ্গী কোম্পানীকে। আমি সরকারী খাজনা তাদের দিয়েছি—সেখানে পাঠাবে বলে। তা ব’লে নবাব আলিবর্দীর পাঞ্জা মোহর দস্তখতী ফরমান নাকচ করে নয়া বন্দোবস্তী? তা হলে তো তাকেই মালেক-ই-মুল্ক বলে মেনে নেওয়া হল। কভি না। নবাবের নিমক খেয়ে, হিন্দু ছিলাম মুসলমান হয়েছি, এখন আবার তা না মেনে নিমক- হারাম হয়? তা’ হলে তো মুসলমান থেকে ফের কেরেস্তান হ’তে হয়। না-এ কভি না হো সক্তা হ্যায়।
শুধু তাই বলেই ক্ষান্ত হন নি তিনি। তিনদিন পর ঠাকুরপাড়ায় ঘোষণা করেছিলেন—আর এখানে এই ঠাকুরপাড়ায় তিনি থাকবেনই না। যেখানে জমীনের মালেক হিসেবে সেলাম আদায় ক’রে আজ তিনপুরুষ কাটিয়ে এলেন, সেখানে খাজনা গেল গেল; সেলাম যেখানে যেতে বসেছে সেখানে আর তিনি থাকবেন না ঠাকুরপাড়ায়। কভি না। এ কভি না হো সক্তা হ্যায়। চলো, ঠাকুরশরীফে গিয়ে বাস করব।
ঠাকুরশরীফ–কাকদ্বীপের কাছে একটা দ্বীপের মত জায়গা। বাকসিদ্ধ গুলমহম্মদ ঠাকুর নবাব মীরকাসেমের প্রথম আমলে নগদ টাকা সেলামী দিয়ে এই দ্বীপটি নানকার হিসেবে একরকম খরিদই করেছিলেন। তখনও মীরকাসেমের সঙ্গে কোম্পানীর ঝগড়া বাধে নি। সে ফরমানে নবাবী মোহরের সঙ্গে কোম্পানীর এক সাহেবের দস্তখত ছিল। কারণ নবাব মীরজাফর কোম্পানীর দেনা শুধতে মেদিনীপুর অঞ্চল কোম্পানীকে ছেড়ে দিয়েছিলেন, সে বন্দোবস্ত মত কোম্পানীর সইয়ের দরকার ছিল। তাতে আপত্তি দিতে কোম্পানীর এতিয়ার ছিল না। তিনি ফিরিঙ্গীকে খাজনা দিতে হবে যে মুলুকে সে মুলুকে বাস করবেন না। দ্বীপটায় কিছু প্রজা ছিল। হজরৎ গুলমহম্মদ ঠাকুরের সমাধি ছিল, আবাদী জমি ছিল। সে প্রায় পাঁচশো বিঘার উপর; সেখানে গিয়ে বাস করবেন তিনি।
তাই করেছিলেন তিনি। এখানকার পাকা ইমারৎ, পুকুর, বাগ-বাগিচা সব ফেলে চলে গিয়েছিলেন ‘ঠাকুরশরীফে’।
সে চলে যাওয়ার কথা শ্যামনগরের লোকের মুখে আজও শুনতে পাওয়া যায় সুলতা! সেদিন নাকি ঠাকুরপাড়ার বাকী লোকেরা পাইকপাড়ার পাইকেরা এমন কি লাট যুগলপুরের ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য সকলে পথের দুপাশে দাঁড়িয়ে সেলাম দিয়েছিল আর কেঁদেছিল।
মাঝলা ঠাকুর হাতীর উপর চেপে গঙ্গার ঘাট পর্যন্ত এসেছিলেন। ছেলেরা এসেছিল ঘোড়ায়, বয়েল গাড়ীতে—মেয়েরা পালকিতে। জ্ঞাতিরাও কয়েক ঘর তাঁর সঙ্গে গিয়েছিল। তাদের পুরুষেরা হেঁটে আর মেয়েরা বয়েল গাড়ীতে। মাঝলা ঠাকুর হাতীর উপর বসে দুধারে মুখ ফিরিয়ে সেলাম ফিরিয়ে দিতে দিতে গিয়েছিলেন-”সেলাম আলায়কুম, সেলাম আলায়কুম, সেলাম আলায়কুম!”
গঙ্গার ঘাটে দেখা হয়েছিল মাধব দে-সরকারের সঙ্গে। দে-সরকার মেদিনীপুর থেকে ফিরছে—লাট যুগলপুরের তালুকদারী সে কোম্পানীর মেদিনীপুর কালেক্টর সাহেব বাহাদুরের কাছ থেকে বন্দোবস্তের কাগজ নিয়ে ফিরছে। সেটা ১৭৯৪ সাল।
খবরটা সে নিজেই দিয়েছিল মাঝলা ঠাকুরকে। সেলাম করেই দিয়েছিল। মাঝলা ঠার এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে বলেছিলেন—তা হ’লে এই বুড়ো হাতীটা তোকে দিয়ে গেলাম মাধব। নতুন জমিদার হলিহাতীতে না চড়লে মানাবে না। তবে এটাকে যেন খেতে দিস। মরা হাতীর লাখ টাকা দামের লোভে না খেতে দিয়ে মেরে ফেলিস না। তা হলে তোকে অভিসম্পাত লাগবে। বুঝলি। আমাদের বংশের সিদ্ধাই তো জানিস!
মাধব দে-সরকার বৈষ্ণব-ফোঁটা তিলক কাটত; গলায় কণ্ঠী পরত। সে খুশী হয়ে সেলাম করে বলেছিল—গোবিন্দর নামে দিব্যি করে বলছি ঠাকুরসাহেব। গলার কণ্ঠী ছুঁয়ে বলছি। দোব—দোব—দোব।
ওদিকে তখন গ্রামে সর্বরক্ষাপাড়ায় ঢাক বাজতে শুরু করেছে। বাজনা শুনে তাড়াতাড়ি নৌকোয় চড়ে ঠাকুরসাহেব বলেছিলেন—জলদি নাও খুলরে মাঝি —জলদি জলদি।
সেদিন ঠাকুর মিঞারা ঠাকুরপাড়া ছেড়ে চলে যাচ্ছেন বলে শ্যামনগরের ব্রাহ্মণসজ্জনে ঢাক বাজিয়ে গ্রামদেবতা সর্বরক্ষের কাছে পুজো দিয়েছিল। তারা খুশী হয়েছিল—এবার মাধব সরকার ভক্ত বৈষ্ণবমানুষ জমিদার হল, এবার তাদের সুখের দিন এল। তারা এবার গুরুর মত থাকবে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই ভুল ভাঙল।
দে-সরকারের গোমস্তা এল আদায় করতে, বসল চণ্ডীমণ্ডপে। থোকা কড়চা খুলে সকলকে খাজনার ফর্দ শোনালে। তিন বছরের খাজনা বাকী। রহমৎ ঠাকুরের সঙ্গে কোম্পানীর যে সময়টা ঝগড়া চলেছে সে সময় কোম্পানীর ঢোল দিয়ে গিয়েছে যে কোম্পানী খাস করলে লাট যুগলপুর। সেই সময় থেকে খাজনা প্রজাও দেয় নি, রহমৎ ঠাকুরও আদায় করেন নি। তিনিই বলেছিলেন, ঠিক বাত, ফয়সালা হোক। তারপর নেওয়া যাবে।
সেই খাজনার সঙ্গে সিকি সুদ চড়িয়ে খাজনা দাবী করলে দে-সরকারের গোমস্তা। ব্রাহ্মণ কায়স্থ সদগোপ প্রজারা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেল।
—সুদ! সুদ কিসের?
-–বাকী খাজনার।
—বাকী খাজনার সুদ? যা ঠাকুরেরা কখনও নেয় নি!
—ঠাকুরসাহেবরা মুসলমান—সুদ তাঁদের কাছে হারাম। শাস্ত্রে নিতে বারণ আছে। কিন্তু তাঁরা যে নানা আবওয়াব নিতেন গো। দে-সরকার কত্তা মহাজনী ক’রে সুদ নিয়ে সামান্য অবস্থা থেকে জমিদার। সুদ তিনি নেবেন। তাঁকে তো কোম্পানীকে তিন বছরের টাকা গুনতে হয়েছে। ঠাকুরসাহেবরা দিতেন বছরে একশো টাকা সরকারী খাজনা, দে সরকার কত্তা দিয়েছেন বছরে সাতশো। সুদ না নিলে জমিদারী রাখবেন কি ক’রে? তাছাড়া বন্দোবস্ত তো এখন বছর বছর। তার মানে কোম্পানী তো বাড়িয়েই যাবে।
ব্রাহ্মণেরা চুপ করে থেকে বলেছিলেন—হুঁ। সুদ না দিলে?
হেসে গোমস্তা—ওলায়েত্ সিরজা-বলেছিল—তা আমি কি করি বলব? দে-সরকার বলবেন। কোম্পানীর হুকুম তো ঢালোয়া হুকুম। খাজনা আদায় জন্যি কি কাণ্ড ঘটতেছে বাংলাদ্যাশে ওকিব (ওয়াকিবহাল) আছেন তো! ধরি আন—বাঁধি রাখ, বুকে কাঠ চাপাও, ব্যাত চালাও, পিঠে ব্যাল কাঁটার ডাল দিয়া পিটো। খাজনা আদায় কর। রেজা খাঁর মতন জবরদস্ত আদমী গেল। এখনও দ্যাওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিং মজুত। নতুন আইন করি দিছে। এখন জমিদার দে-সরকারের মরজি। শুনতেছি ইবার কোম্পানী আইন করতেছে, পাকা ধান মাঠে আটক দিয়া খাজনা আদায় করাবার আইন করবেন। বললাম তো, এ্যাখন প্রজার মতি আর জমিদারের তাগদ। তবে মরজি বলে একটা বাহ্ আছে। এ্যাই তো আমাদের ঠাকুরসাহেবের দিল সায় দিলে না, মরজি উঠল না, ছেড়ে দিলে ঝুটা চীজের মতুন।
গোমস্তাটি পাকা গোমস্তা। দে সরকার তাকে হিজলীর নবাববংশের যে ছিটেফোঁটা তখনও ছিল, তাদের সেরেস্তা থেকে এনে বহাল করেছিলেন। তাঁর সেরেস্তায় তিনি গ্রামের দু-চারজন জাতি-জ্ঞাতির মধ্য থেকে নিয়েছিলেন, তারা নিতান্তই ছিল নিরীহ আমলা, যে সেরেস্তা হাতের মুঠোয় কাবেজে থাকে সেই রকম লোক সেরেস্তায় রেখেছিলেন। যেমন খাজাঞ্চি, হিসেবনবীশ, খাস জোত তদারকদার, গরুবাছুর তদারকদার—এইসব কাজ করত তারা। বাকী কাজ, যেখানে প্রজার সঙ্গে কারবার, নায়েব গোমস্তা এসব ছিল মুসলমান এবং অন্য জায়গার লোক—যাদের পক্ষে ব্রাহ্মণ কায়স্থ বা গ্রামের লোক বলে চক্ষুলজ্জার কোন কারণ নেই।
গোমস্তা ওয়ালে মিরজার কথার জবাব ব্রাহ্মণেরা ঠিক খুঁজে পান নি। বাংলাদেশে দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিং, রেজা খাঁর খাজনা আদায়ের অত্যাচারের কথা তাঁদের অজানা ছিল না। তাঁরা সেদিন বুঝতে পেরেছিলেন, ঠাকুর মিঞাদের তালুকদারীর মধ্যে তাঁরা কতটা সুখে এবং নিরাপদে ছিলেন। তবু তাঁরা হাল ছাড়েন নি। তাঁরা দল বেঁধে গিয়েছিলেন রাধানগর-দে-সরকারের বাড়ী। দে-সরকারের বাড়ী তখনও কাঁচা দেওয়ালের উপর খড়ের চালের বাড়ী। কেবল একতলা একটি দালানে রাধাগোবিন্দ, নিত্যানন্দ এবং জগন্নাথের সেবা প্রতিষ্ঠা করেছেন। সামনে খড়ের আটচালা। আটচালার সামনে খড়েরই একখানা ওই আটচালার মতই সেরেস্তাখানা, তাও হালে তৈরী হয়েছে। সেইখানে তক্তাপোশে ফরাস করে তাকিয়া হেলান দিয়ে বসে কাছারী করেন। নিচে আটচালার মেঝের উপর তালপাতার চাটাই খেজুর চাটাই বিছানো একদিকে আর দুখানা তক্তাপোশের উপর শতরঞ্চ বিছানো।
ব্রাহ্মণেরা যখন পৌঁছুলেন, তখন ওই সেরেস্তাখানা কাছারীর সামনে মাধব দে সরকার বাঁ হাতে রূপো বাঁধানো হুঁকো ধরে তামাক খাচ্ছিলেন আর সামনে বাগিচার পত্তন করছিলেন —নারকেলের বাগান লাগাবেন। পরনে থান ধুতি; তখন বিলিতী রেলির কলের কাপড় আমদানী হয়েছে; পায়ে চটি; গায়ে একটা মেরজাই। কপালে তিলক, গলায় কণ্ঠী, তার সঙ্গে একটি সোনার সরু হার চিকচিক করছে।
ব্রাহ্মণদের দেখেই সমাদর করে দে সরকার আহ্বান করে বললেন—আসুন আসুন আসুন। পবিত্র হল আমার নতুন কাছারী। বলেই হুঁকো বাঁ হাতে ধরেই হেঁট হ’তে চেষ্টা করে বললেন—ওঃ! কাতর আর্তনাদ ক’রে উঠলেন। তারপর সেই স্বল্প একটু হেঁট অবস্থাতেই ডান হাত কপালে ঠেকিয়ে বললেন—ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ। কোমরে এমন দাকো দরদ লেগেছে —ওঃ! বলে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন।
হেসে সুরেশ্বর বললে—ব্রাহ্মণেরা সেকালের ইন্টেলেক্চুয়েল। একালের ইন্টেলেকচুয়েলের মতই চতুর। দে-সরকারের মুখে একসঙ্গে হাসি এবং যন্ত্রণার অভিনয় তাঁদের দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারে নি। মুহূর্তেই তাঁদের চিত্ত বিরূপ হয়ে উঠেছিল। তাঁরা প্রত্যাশা করেছিলেন—বৈষ্ণবধর্মাবলম্বী ফোঁটাতিলক কাটা দে সরকার পূর্বের মতই তাঁদের পায়ের ধুলো নিয়ে মুখে বুকে ঠেকাবেন। কিন্তু বুঝলেন, জমিদার দে-সরকার তাঁদের আর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করবেন না। দে-সরকার এই কদিনের মধ্যেই জমিদার হয়ে দ্বিতীয় জন্ম নিয়েছে। সে দে-সরকার মরে বেঁচেছেন। ব্রাহ্মণ দলের অগ্রণী ছিলেন তখন জনার্দন ভট্টাচার্য, বিমলাকান্তের মাতামহ পদ্মনাভ ভট্টাচার্যের পিতামহ, তিনি বৃদ্ধ তখন, কিন্তু খাঁটি বামুনে তেজ তাঁর ছিল। তিনি বলেছিলেন—হয়েছে বাবা মাধব! ওই ঢের। ওতেই আশীর্বাদ করছি। তা বড়ই দুঃখের কথা। কোমরে দাকো বাত ধরলো। তা ধরে। তা ধরে। বিষয়ের বোঝা যখন ঘ্যাঁচ করে মাথায় চাপে, তখন দুর্বল মানুষ হ’লে খ্যাঁচ ক’রে কোমরে দাকো বাত ধরে যায়। ও আর সারে না বাবা! তা বেশ! ঘোড়ার কুমড়ে, বিষয়ীর দাকো আর বামুনের পায়ে ফাট, এ নাহলে মানায় না বাবা। কিন্তু এক কাজ করতে পারো বাবা, কোম্পানীর চরণ ঠেকিয়ে নিতে পার ওখানে, শুনেছি কোম্পানী নাকি ‘পাদুকো’। মানে ভূমিষ্ঠ হবার সময় মাথায় আগে ভূমিতে ঠেকেনি, পা আগে ঠেকেছিল, নইলে পৃথিবী দলন করবার শক্তি পাবেন কোথা থেকে। নিশ্চয় ‘পাদুকো’ ওরা, তুমি খবর নিয়ো।
ব্রাহ্মণেরা বাকপটু—সেখানে তাঁরা যত চতুর, তার থেকে বিষয়কর্মে এবং বাস্তবতা বোধে অনেকগুণে চতুর দে-সরকার। তিনি শ্লেষকেও শ্লেষ বলেই ধরেন নি। সুবুদ্ধির মতো হেসে বলেছিলেন—বড় ভাল বলেছেন, বড় ভাল বলেছেন। কোম্পানীর জন্মকালে যদি পা দুটোই সর্বাগ্রে সদম্ভে মাটিতে পড়ে না থাকে, তবে দুনিয়া পদদলিত ক’রে বেড়াচ্ছে কি ক’রে? ঠিক কথা। ভাববার কথা!
আটচালায় এনে সমাদর করে শতরঞ্চ পাতা তক্তাপোশের উপর বসিয়ে কড়িবাঁধা ডাবাহুঁকোয় তামাক খাইয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—তারপর, সকলে মিলে আপনারা এই সময় মানে।
সমস্ত কথা শুনবার আগেই দে-সরকার সব জানতেন, তিনি প্রস্তুত হয়েই ছিলেন এবং লোহা উত্তপ্ত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় সে সুতীক্ষ্ণ বোধ তাঁর ছিল, তিনি সেই মুহূর্তের অপেক্ষা করে শুনেই যাচ্ছিলেন বিবরণ এবং ঠিক মুহূর্তটিতে এতখানি জিভ কেটে বলেছিলেন- রাধামাধব, রাধামাধব, রাধামাধব হে, আপনারা ব্রাহ্মণ, আপনাদের কাছে সুদ গোমস্তা ‘ওয়ালে মির্জা’ হাজার হলেও তো হিন্দু নয়! ও ঠিক বুঝতে পারে নি। তাই কি হয়? আপনাদের সুদ নাই, আপনারা ব্রাহ্মণ, আপনারাও তামাদি বলবেন না। ও যেমন ঠাকুরদের সময় ছিল, তেমনি চলবে। তবে —।
ব্রাহ্মণরা, এমন কি একালের ইন্টেলেকচুয়েলরাও বিষয়বুদ্ধিতে ভোঁতা বললে রাগ করো না সুলতা। ১৯৩৭ সালেই সেটেলমেন্টে পলিটিক্যাল ইন্টেলেকচুয়ালদের কেমন ক’রে ঠকিয়েছিল কল্যাণেশ্বর, সে বলব তোমাকে যথাসময়ে।
এখন আবার সেকালে ফিরে চল। ব্রাহ্মণেরা ওই ক’টি কথাতেই উত্তপ্ত অবস্থা থেকে ঠাণ্ডা হয়ে এসেছিলেন।
পদ্মনাভ ভট্টাচার্য বলেছিলেন—আবার তবে রাখছ কেন বাবা? তবে-টা কি ব্যক্ত কর!
–বলছি—মানে, দেখুন, আমাকে সম্পত্তি বজায় রাখতে হবে। তাতে সুদ ব্রাহ্মণের কাছে না নিয়ে চালাব, তাতে আমার ধর্ম আছে। কিন্তু সকলকে মানে দোরবস্তু প্রজার -! তবে-টা আমার তৎসম্পর্কে!
ব্রাহ্মণেরা হেরে গেলেন। একমুহূর্তে ধর্মপ্রাণ দে-সরকারের দুঃখ অনুমান করে বললেন—নিশ্চয়-নিশ্চয়। এতে কথা কি আছে! নিশ্চয়!
দে-সরকার নিবেদন করলেন—তা হলে নিবেদন নাই। আমি বলি কি—আপনারা খাজনা বাবদ তঙ্কা আমানত রাখুন। আমানতি রোকা নিন। তারপর হিসাব-নিকাশ ক’রে চেক রসিদ দেওয়া হবে।
খুশী হয়ে ব্রাহ্মণেরা উঠে এলেন। দে-সরকার কোমরে দাকো ব্যথা নিয়ে কোনক্রমে ঈষৎ হেঁট হয়ে ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ বলে প্রণাম সারলেন। এবার ব্রাহ্মণেরা অখুশী হলেন না।
ঠাকুর মিঞাদের সেলাম দিতে হত, সেটা দিতে হল না আর, সঙ্গে সঙ্গে দে-সরকারের কাছে প্রাপ্য প্রণামটা গেল। আর আমানতের প্যাঁচে পড়লেন। সুদ রেহাইয়ের বদলে, হিসাবের বদলে, ঠাকুর মিঞাদের আমলের যার যত বাকী ছিল, তাও দেয় দাঁড়াল।
তখন তাঁরা জ্ঞানচক্ষু বিস্ফারিত করে দাঁড়ালেন। ইতিমধ্যে ঝগড়াটা আরও পাকল সর্বরক্ষেতলার বলি নিয়ে।
সর্বরক্ষাদেবী গ্রামদেবতা। শক্তি মূর্তি, একখণ্ড পাথর। তাতে মুখ হাত পরিয়ে কাপড় দিয়ে সাজিয়ে বিজয়াদশমীতে, মাঘী পূর্ণিমাতে পুজা হয় বলি হয়। সেবায়েত চিরকাল জমিদার। কিন্তু ঠাকুরেরা মুসলমান বলে তাঁদের নামে সংকল্প ছিল না। আগের কাল থেকে জমিদারের দেওয়া জমি বাবদ একজন প্রজা একটি পাঁঠা এনে দিত। বলি হত। সংকল্প হত গ্রামবাসী প্রধানতম ব্রাহ্মণের নামে, তিনিই পেতেন ওই বলির প্রসাদ। দে-সরকারের সঙ্গে ঝগড়া লাগল এই নিয়ে। দে-সরকার বললেন-আমি হিন্দু জমিদার। এখন সংকল্প আমার নামে হবে। বলি আমি পাব।
আর ঝগড়া হ’ল ষষ্ঠীতলায়। ষষ্ঠীতলায় পুজোর সময় দে-সরকার-গিন্নী অষ্টাঙ্গে গয়না প’রে বউ বেটী নিয়ে এসে ভটচাজবাড়ীর গিন্নীদের সামনে দাঁড়ালেন। সঙ্গের কর্মচারী বললে—ঠাকুরুণরা একটু সরে বসবেন গো! রাণী-মা এয়েছেন। ওনার পুজো হয়ে যাক আগে, তারপর আপনারা সব পুজো করবেন। বাড়িতে জামাইবাবুরা এসেছেন। বসে আছেন। কত্তা হুকুমও দিয়েছেন—তাঁর বাড়ীর পুজো আগে হবেন।
সেকালের ব্রাহ্মণগৃহিণী তাঁরা-লাল সুতো হাতে বেঁধে কৃষ্ণনগরের মহারাণীর গায়ে জল ছিটিয়ে দেমাক করে বলে এসেছিলেন—আমার হাতের লাল সুতো আছে তাই বাংলাদেশের মান আছে। গ্রাহ্যও করেন নি মহারাণীকে। তা এ তো দে-সরকার। কে একজন প্রখরা ব্রাহ্মণকন্যা বলে উঠেছিল-দাঁড়াতে বল রে মুখপোড়া—দাঁড়াতে বল তোর চামচিকে রাজার চামচিকে রাণীকে। দে-সরকার যদি রাজা হয় তবে চামচিকেও পক্ষীদের রাজা। রাণী-মা! মরণ, তোদের জিভে আর কিছু আটকায় না।
তাঁরা সরে তো বসেনই নি বরং ইচ্ছে করে দেরী করেছিলেন—ঠায় রোদে দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন দে-সরকার-রাণীকে।
ঝগড়া এরপর থেকেই বাধল। দে সরকার সুযোগ পেলেন সুদ সমেত বকেয়া আদায়ের। কোম্পানীর পারমানেন্ট সেটেলমেন্টের আমল। জমিদার যারা খাজনা নিয়মিত যোগায়, তাদের খাতির করে কোম্পানী। দে-সরকারের মোটা খাস জোত ছিল। গোটা ঠাকুরপাড়ার ঠাকুরদের নানকার তিনি আত্মসাৎ করেছেন। তার সঙ্গে মহাজনী। তিনি মামলা মকদ্দমা করেও বছর বছর কিস্তিমাফিক খাজনা যুগিয়ে যান। জানেন সবুরে মেওয়া ফলে। আর জানেন হাতে মারার চেয়ে ভাতে মারাই মোক্ষম মার। তারপর লর্ড বেন্টিঙ্কের আমলে মুনসেফী আদালতের ছত্রছায়ায় আশ্রয় পেয়ে মামলায় মামলায় ব্রাহ্মণদের পাকে পাকে প্যাঁচ কষতে শুরু করেছিলেন।
ব্রাহ্মণেরা কিন্তু আশ্চর্য জাত। তাঁরা প্যাঁচে পড়েও প্যাঁচ ছাড়ালেন উল্টো প্যাঁচ ক’ষে। গোটা যুগলপুর লাটের মুসলমান সদগোপ- ব্রাত্যদের এক করে আশ্চর্য একটি জোট বেঁধে তুললেন। শেষ পর্যন্ত দে-সরকার একটা মিটমাট করতে বাধ্য হল।
ব্রাহ্মণদের সুদ উঠিয়ে দিয়েছিলেন। বকেয়া খাজনা যা দাবী করেছিলেন দে-সরকার ঠাকুর মিঞাদের আমলের বাকী জড়িয়ে, তাও ছেড়ে দিয়েছিলেন। এবং বৃদ্ধির দাবী আর তুলতেই সাহস করেন নি। শেষ বয়সে হঠাৎ পঙ্গু হয়েছিলেন মাধব দে সরকার, তাতে তাঁর ধারণা হয়েছিল যে, ব্রাহ্মণদের শাপে এই ব্যাধি ধরেছে তাঁর।
তারপর তাঁর ছেলে নিতাই দে সরকার, সেই ট্যারা মানুষটি, যে ব্যক্তিটি সোমেশ্বর রায়ের কাছে পদ্মনাভ ভট্টাচার্যের বাকী খাজনার টাকা পাইপয়সা গুনে নিয়ে খুঁটে বেঁধে প্রণাম করে চলে গিয়েছিল। নিতাই দে-সরকার মাধব দে-সরকার থেকে গুণী মানুষ ছিল জমিদার হিসেবে। যে প্রণাম উঠিয়ে দিয়েছিলেন মাধব দে সরকার কোমরে দাকো বাতের জন্যে, সে বাতকে সে প্রশ্রয় দেয় নি। অজস্র প্রণাম দিয়ে সে শেষ পর্যন্ত নামমাত্র একটা বৃদ্ধি, টাকায় দু-আনা, তা সকলের সম্মতি নিয়ে আদায়ও করলে। কিন্তু তাতে খুশী হল না। টাকায় দু আনা বৃদ্ধি! এ যে ভিক্ষে নেওয়া হল। তবু অধীর সে হল না। সুযোগ মিলল।
১৮৫৮ সালে সিপাহী বিদ্রোহের পর দে সরকার সে সুযোগ পেলে। জন রবিনসন এসে তাকে মহাজন ধরলে। কুঠী চালাবার জন্যে টাকা চাই। টাকার উপর মোটা সুদ। বছরখানেক চড়া সুদে টাকা নিলে কুঠী চালাবার জন্যে। সময়মত শোধও দিলে। দে সরকার লোকটাকে এক বছরে বাজিয়ে চিনে নিলে।
মিউটিনির পর ভারতবর্ষ ইংলন্ডেশ্বরীর খাসমহল হতেই দাপট বাড়ল ইংরেজদের। তার সঙ্গে জন রবিনসনের হাত লম্বা হয়ে উঠল। দুটো কুঠী তার ছিল। কিন্তু চলত না খুব ভাল। মদ আর ব্রাত্য নারীর নেশায় ব্যবসা সে ঠিক চালাতে পারত না। দে সরকার টাকার কারবার করতে করতে বললে—সাহেব, তুমি যুগলপুরে কুঠী কর। আমার জমিদারী, আমি তোমাকে সাহায্য করব। টাকা দোব। ওখানকার জমিতে এখান থেকে অনেক ভাল নীল জন্মাবে।
জন রবিনসন ওখানে ঠাকুরপাড়ায় কুঠীর পত্তন করলে।
দে-সরকারের আর একটা উদ্দেশ্য ছিল, সেটা ওই সাহেবের খুঁটির জোরে ওই যুগলপুরের ব্রাহ্মণদের সে শায়েস্তা করবে।
তখন লালমুখ সাহেব কলির দেবতা হয়ে উঠেছে এদেশের মানুষের কাছে। জন রবিন সনের আর একটা উৎসাহের কারণ ছিল। এখানে পাকপাড়ার নারী।
কিছুদিনের মধ্যেই রবিনসনের ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দে এবং ধুলোয় যুগলপুরের মানুষ ব্রাহ্মণ কায়স্থ সকলে চকিত হয়ে উঠল। জমিতে জবরদস্তি নীল বোনা আরম্ভ হল। পাইকে ভরে উঠল নীল কুঠী। ব্রাহ্মণেরা মাথায় হাত দিয়ে বসল। দে সরকার পালকি চড়তে শুরু করলে। দু পাশে পাইক না নিয়ে হাঁটে না। দ্বিতীয় বৎসরে বিমলাকান্তের জমিতে জবরদস্তি নীল পড়ল।
ঠাকুরদাস পাল তখন পঁয়ত্রিশ বছরের জোয়ান। তার অহঙ্কার ছিল কীর্তিহাটের জামাই এবং শরিক বিমলাকান্তের জোতদার সে! তার জমিতে বাঘেরও ধান খাবার ক্ষমতা নেই। হঠাৎ তার জমিতে নীল বুনতেই সে চিঠি লিখলে কাশীতে বিমলাকান্তকে।
—”এ অপমানের অত্যাচারের প্রতিকার না হইলে সে জমি করিতে পারিবে না। যাহা হয় প্রতিকার করিতে আজ্ঞা হয়। একবার না আসিলে প্রতিকার হইরে না। ইতি সেবক—শ্রীঠাকুরদাস পাল।”
কিছুদিন পর শ্যামনগরের ঘাটে এসে একখানা নৌকা লাগল। নৌকা থেকে নামলেন বিমলাকান্ত নয়, আঠারো-উনিশ বছরের “কমলাকান্ত”। সুন্দর সুপুরুষ—গৌরকান্তি-কাশীর জলহাওয়ায় আর ব্যায়ামে গড়া শক্ত দেহ। উজ্জ্বল দীপ্ত উগ্র চোখ। নাকের ডগাটি ঈষৎ স্থূল।
অনেকটা বিমলাকান্তের মত। আবার যারা বীরেশ্বর রায়কে দেখেছে, তারা বলবে চোখের দৃষ্টি আর নাকের ডগার ঈষৎ স্থূলতার মধ্যে তাঁর স্পষ্ট আদল। বাবা আর মামার মত একই সঙ্গে!
তোমাকে যেমনভাবে বলে যাচ্ছি সুলতা, ঠিক এমনিভাবেই সেদিন কীর্তিহাটের রায়বংশের সত্যটি আমার মনের সামনে একটির পর একটি করে ভেসে উঠেছিল। সেদিন গোয়ানপাড়ায় যে ঘটনা ঘটল, তার প্রতিক্রিয়ায় মনের মধ্যে এই অতীত কাহিনী ভিড় করে মুখ বাড়িয়ে কখনও ভয় দেখাচ্ছিল, কখনও যেন সজল চোখে আমাকে বলছিল—–এর প্রায়শ্চিত্ত তুমি করো। তুমি করো। আবার এক-এক সময় বলছিল —মিথ্যের কবরে চাপা পড়ে আমরা মুক্তি পাচ্ছি না। কবর খুঁড়ে তুলে আমাদের মুক্তি দাও।
কাঁসাই তখন বিস্তীর্ণ বালির রাশি। এক পাড় থেকে আর এক পাড় পর্যন্ত পথ অনেকটা, গোয়ানপাড়ার পাড়ে ভাঙন, লাল কাঁকর আর কাঁকর-জমা পাথরের চাঁইয়ে-চাঁইয়ে বাঁধা পড়েছে। ওদিকে একটা স্রোত। তারপর খানিকটা চড়া, সেখানে কিছু চাষ হয়। তারপর এদিকে কীর্তিহাটের দিকে আর একটা স্রোত, তারপর এদিকেও লাল কাঁকর আর পাথরের চাঁইয়ে গড়া শক্ত পাড়। ওদিকে সিদ্ধপীঠের জঙ্গল। সেখানে শালবন, বনকদম, শিমুলের গাছ, বেউড় বাঁশের ঝাড়, এদিকে কীর্তিহাটে বিবিমহলের বাঁধানো পোস্তার নীচে বড় বড় সেগুন গাছের জঙ্গল। তার অনেক বড় গাছ কেটে মেজোতরফ বিক্রী করেছেন; তার শেকড় এবং বীজ পড়ে অসংখ্য চারা হয়েছে, সেও একটা ছোটখাটো জঙ্গল। এইখানে এসেই গোয়ান মেয়েগুলো মেজদির সঙ্গে কথা বলত। একটা দহ আছে বিবিমহলের বাঁধা ঘাটে, সেখানে সাঁতার দিতে আসত গ্রীষ্মের দুপুরবেলা; এখান থেকেই কাল রাত্রে আমাকে ডেকেছিল ওই হ্যারিস।
এই এতটা পথ বালি ভেঙে এসেছিলাম আমি অতীতের ভুতে পাওয়া মানুষের মত। কেবল ওই মুখগুলো দেখেছিলাম। ওই ঘাটে এসে ঠিক তুমি যে প্রশ্ন করলে একটু আগে, ঠিক সেই প্রশ্ন আমারও মনে জেগেছিল। রায় ভটচাজ বংশের এই ধারা, সত্যই কি ওই মহাশক্তির অভিশাপ, না হেরিডিটির প্রভাব, না উপচে-পড়া সম্পদের বিষক্রিয়া? কিছুতেই ওই অভিশাপের কথাটাকে উপেক্ষা করতে পারি নি। ওইটেকেই আমার সবচেয়ে বড় মনে হয়েছিল।
তাই বাড়ী এসেই চিঠির দপ্তর খুলে বসে সমস্তটা আগাগোড়া পড়তে শুরু করেছিলাম। তোমাকে বলেছি—পুলিশ এসে ঘর খানাতল্লাস করতে গিয়ে অতুলেশ্বরের বিরুদ্ধে কিছু পায় নি, কিন্তু ওই কাঁকড়াবিছে-ভরা দামী সেগুন কাঠের সিন্দুক ভর্তি চিঠির দপ্তর বের করে দিয়ে গিয়েছিল। আমি একটি একটি করে পড়ে, রায়বংশের এই ইতিহাসটুকু বের করে সাজিয়ে-গুছিয়ে রেখে দিয়েছিলাম।
১৮৫৯ সালের জানুয়ারী মাসের একখানা চিঠি পেয়েছিলাম, মস্ত মোটা চিঠি, চিঠিখানা কাশী থেকে বিমলাকান্ত ভট্টাচার্য লিখেছিলেন রায়বাড়ীর কুলপুরোহিত রামব্রহ্ম ন্যায়রত্নকে।
আজ কথা আরম্ভ করবার সময় যে রেশমী কাপড়ে বাঁধা কাগজের বান্ডিলটা টেবিলের উপর রেখে বসেছিল, সেটার বাঁধন খুলতে খুলতে সুরেশ্বর বললে—পূর্বেই বলেছি, ১৮৫৭ সালে এখানে এসে সিপাহী বিদ্রোহের বিভীষিকা মিটলে বীরেশ্বর রায় জমিদারী নিয়ে প্রমত্ত হয়ে পড়েছিলেন। না পড়েই যা কি করবেন। জীবনে তখন তাঁর নারীর নেশা কেটেছে। কাটিয়ে দিয়েছে সোফিয়া বাঈ। জীবন নেশা নইলে কাটে না। নেশা তখনই দরকার হয় না যখন পেটের ভাত জোটে না।
পেটে দুবেলা দুমুঠো অন্ন জুটলে তখন আর নেশা নইলে জীবন কাটে না। হয় ভগবান, নয় নারী, নয় বিষয়।
বীরেশ্বর রায়ের ভগবান নেশা ছেলেবেলা থেকে ছিল না। নারীর নেশাও কেটেছে। সুতরাং বিষয়, তাকেই আঁকড়ে ধরেছিলেন। যেটাকে সংসারে নেশার জিনিস বলে অর্থাৎ সুরা, সেটা হল নেশার ক্ষুধা বাড়াবার ওষুধ। ভগবান ভজতে গিয়েও মদ খায়, নারী নেশাতেও মদ নইলে চলে না, বিষয়ের নেশাতেও ওটা চাই। অন্তত ভূ-সম্পত্তি নিয়ে যারা মাতে সেকালে তাদের শতকরা নব্বুইজন মদ্যপানে ক্ষুধা বাড়াত।
বীরেশ্বর রায় ওই দুটিকে সম্বল করে কীর্তিহাটের কাছারীর জাঁকজমক বাড়িয়ে জেঁকে বসেছেন। কলকাতা থেকে খানসামা ছিলমবরদার, খিদমতগার, আর্দালী হরকরা, চাপরাসী, দারোয়ান এনেছেন। দেউড়ীতে পেটা ঘড়িতে ঘণ্টা পড়ে ঘণ্টায় ঘণ্টায়। মামলা সেরেস্তা প্রকাণ্ড করে ফেঁদেছেন; জমিদারী সেরেস্তার আর একটা ফ্যাঁকড়া বেরিয়েছে, দাদন সেরেস্তা। নায়েব গিরীন্দ্র আচার্যির নাম হয়েছে ম্যানেজার, তাছাড়া খাজাঞ্চী সেরেস্তা, হিসাব-নিকাশ সেরেস্তা চিরকাল ছিল, তারও কায়দা-কানুন বেড়েছে। নতুন ঘরবাড়ীর পত্তন হয়েছে। পুরনো ঘরবাড়ী মেরামত হয়ে ঝকঝক করছে। আস্তাবলে ঘোড়া এসেছে, গাড়ী এসেছে। হাতী ছিল গোড়া থেকে, আরও একটা হাতী কিনেছেন। আশাসোঁটা, তাও কিনেছেন নতুন করে।
কাছারী কালীমন্দিরের নাটমন্দিরের দক্ষিণে এবং পূর্বে সারি-সারি ঘরে বসত। তার ঘরদোর বেড়েছে। নতুন আসবাবে নতুন ঢঙে সাজানো হয়েছে, আসবাব খাস সাহেবী দোকানের, ঢঙও সাহেবী। ঘরে ঘরে ক্লক ঘড়ি। সেগুলি একসঙ্গে বাজা চাই। মিনিটে মিনিটে মিল চাই। তার জন্য আলাদা লোক। এ বিবিমহল, সায়েব-সুবার জন্য নির্দিষ্ট। ম্যাজিস্ট্রেট, কালেক্টার, এস-পি, ডেপুটি সাহেবরা আসবেন, এখানে থাকবেন।
বীরেশ্বর রায় কালীবাড়ী সংলগ্ন কাছারীতে বড় একটা আসতেন না। প্রণাম করতে হবে বলে আসতেন না। তিনি কালীবাড়ী এবং কাছারীর লাগোয়া যে প্রথম অন্দরমহল সেখানেই থাকতেন, সেখানেই ছিল তাঁর কাছারী। রায়বাড়ী, রায়বংশের আর কেউ নেই। থাকবার মধ্যে তাঁর মা রাজকুমারী কাত্যায়নী দেবীর দুরসম্পর্কের দশ-বারোটি পোষ্য-পোষ্যা। তার মধ্যে বৃদ্ধ বিধবার সংখ্যা বেশী। তারা বিমলাকান্তের জন্য তৈরী পিছনের মহলটায় থাকত।
সেদিন সকালবেলায় বীরেশ্বর রায় বসে মামলা সেরেস্তার কাগজ দেখছিলেন। পাশে বসেছিলেন ম্যানেজার গিরীন্দ্র আচার্য আর মামলা সেরেস্তার নায়েব। পরামর্শ চলছিল, গোপাল সিংয়ের মকদ্দমা নিয়ে।
গোপাল সিং—মণ্ডলান আদায়ী মহাল-বীরপুরের মণ্ডল। তাকে উচ্ছেদ করে মৌজা বীরপুর খাস আদায়ে আনতে হবে। তার জন্য এক বীরপুর মহলে চারশো নম্বর বাকী খাজনার মামলা দায়ের হয়েছে। এ ছাড়া খোদ গোপাল সিংয়ের সঙ্গে দেওয়ানী, ফৌজদারী জড়িয়ে পঁচিশ নম্বর মামলা।
অবস্থাটা একটু জটিল হয়ে উঠেছে। প্রজারা সকলেই গোপাল সিংয়ের বশীভূত। তারা বলছে, মণ্ডল গোপাল সিংয়ের হাতে খাজনা দেয় বরাবর, তারা তাকেই জানে, তার সঙ্গেই তাদের বন্দোবস্ত, তাকে ছাড়া অন্য কাউকে খাজনা দেবে না। জমিদারকে খাজনা দেবে গোপাল সিং।
বীরেশ্বর রায় বসে ভাবছেন। গিরীন্দ্র আচার্য নিজের মাথার তালু নখ দিয়ে ক্রমাগত চুলকে যাচ্ছেন। মামলা সেরেস্তার নায়েব আসনপিঁড়ি হয়ে বসে ভাবছেন।
প্রজারা একথা সকলে বললে-মণ্ডলান উচ্ছেদ হওয়া শক্ত হবে।
বীরপুর মৌজার মণ্ডল জমিদারকে আদায় দেয় দেড় হাজার টাকা। নিজের থাকে প্রায় পাঁচশো। উচ্ছেদ হলে এই আদায় হাসতে হাসতে তিন হাজারে দাঁড়াবে। কিন্তু সে কথাটা বড় নয়। বড় কথা, গোপালের মণ্ডলগিরি ঘোচাতে হবে। না হলে অপমানের শোধ হবে না। গোপালকে এনে কাছারীতে বসাতে হবে মেঝের উপর মাদুরের আসনে।
বীরেশ্বরের সোজা হিসেব। হেরে হারানো। মুন্সেফ কোর্টে হারলে জর্জ কোর্ট, সেখানে হারলে হাইকোর্ট। তমলুক থেকে মেদিনীপুর, সেখান থেকে কলকাতা। চলুক না প্রজা কত চলতে পারে!
আচার্য হঠাৎ মাথা চুলকানো বন্ধ করে বললে-এক কাজ করা হোক।
বীরেশ্বর রায় তাঁর মুখের দিকে তাকালেন। নায়েব সোজা হয়ে বসল। আচার্য নায়েবের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন—মামলার শমন সমস্ত গায়েব করে পেয়াদাকে দিয়ে জারী হইল, রিটার্ন লিখিয়ে দাও। বুঝেছ?
—আজ্ঞে।
—তারপর ডিগ্রী হোক একতরফা। বুঝেছ?
—আজ্ঞে।
—কতক ডিগ্রী হোক। কতক মামলার মাঝখানেই টাকা দাখিল হোক।
—আজ্ঞে?
—বুঝলে না? আমরাই প্রজার নামে টাকা দাখিল করলাম! বুঝেছ?
—বুঝেছি। আজ্ঞে হ্যাঁ। এবার বুঝেছি!
—যা ডিগ্রী হল, তার কতকগুলোতে আমরাই টাকা দাখিল করলাম। ঘরের টাকা ঘরে এল। দু-চার কি দশ নম্বর রেখে দাও; তামাদির মুখে-মুখে জারী করে জিইয়ে রাখ! বুঝেছ?
—আজ্ঞে হ্যাঁ। জলের মত। এ মোক্ষম পথ! হ্যাঁ আজ্ঞে, এর আর মার নেই। প্রজাদের জমিদারের সঙ্গে সম্বন্ধ স্বীকার হয়ে গেল। আজ্ঞে হ্যাঁ, আমাদেরও হারও হল না।
—বাবা বীরেশ্বর, তুমি কি বল?
বীরেশ্বর বললেন—তা তো হল সব। কিন্তু প্রজার খরচ হল না, অবস্থায় তারা দুর্বল হল না।
—’ধৈর্য ধরতে হবে বাবা।’ তিনি আঙুল তুলে বললে তিন বছর। তিন বছর পর নীলেম উচ্ছেদ দুই মামলাতে জড়িয়ে দোব। এদিকে খোদ গোপালের সঙ্গে চলুক ফৌজদারী দেওয়ানী। সুলতার চোখ দুটি বিস্ফারিত হয়ে উঠেছিল বিস্ময়ে। তার দিকে তাকিয়ে সুরেশ্বর বললে—বিস্মিত হচ্ছ তুমি?
সুলতা বললে—তা হচ্ছি। না হলেই বিস্ময়ের কারণ হত আমার পক্ষে।
সুরেশ্বর বললে—তখন ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজত্ব established by law : সামন্ত ভূস্বামীরা জমিদারে পরিণত হয়েছেন, might is right-সেটা একমাত্র ইংরেজের। ভূস্বামীদের বিদ্রোহ দমনে লাঠি চার্জের right নেই। যা কর আদালত মারফত। তাঁদের যুদ্ধপিপাসা মেটাবার রণক্ষেত্র তখন একটিই। আদালত। মকদ্দমাই তখন যুদ্ধ। এ যুদ্ধে রক্তক্ষয় হয় না, রক্তশোষণ হয়। ফর্মটা পাল্টেছে। গিরিয়ার যুদ্ধে আলীবর্দী খাঁ রুমালে পাতলা ইট বেঁধে সরফরাজ খাঁর কাছে পাঠিয়েছিলেন কোরান বলে, পলাশীর যুদ্ধে মীরজাফর যুদ্ধবিরতির আদেশ দিয়েছিল, ক্লাইভ সাদা ফ্ল্যাগ দেখিয়েছে বলে। যুধিষ্ঠির যে যুধিষ্ঠির, দ্রোণ গুরুকে বধ করবার সময় অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ বলেছিলেন। প্রেমের কথা এক্ষেত্রে তুলব না। কিন্তু যুদ্ধে এ আছেই। তোমাদের নতুনকালে এ মামলাযুদ্ধ গৌণ হয়ে ভোটযুদ্ধ বড় হয়েছে। বল তো সুলতা, হলফ করে, সে যুদ্ধে ফল্স ভোটিং হয় কিনা! রাগ করো না। আমি জমিদারীর স্বপক্ষে আদৌ নই। আমি খুশী হয়েছি। আজই আমার জ্ঞাতিরা এসেছিল, জমিদারী উচ্ছেদ হচ্ছে, আইনটা বলবৎ হবার আগে তারা জমিদারীর অন্তর্গত খাস জোত, খাস পতিত ভুয়ো চেক কেটে রায়বংশের নানাজনের নামে প্রজাপত্তন করতে চায়। তাতে জমিদারী গেলেও আসল বস্তু জমির একটা বড় অংশ রায়বংশের দখলেই থেকে যাবে। কিন্তু তাদের সে প্রস্তাবে আমি রাজী হইনি। কমলেশ তারই জন্য দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে আমাকে গাল দিচ্ছিল, তাও দেখে গেছ। তার হয়ে তোমার কাছে মাফ চেয়েছি, বলেছি—ও ইতর, নেশাখোর। তার সঙ্গে এটা বলিনি যে, কমলেশ একজন উৎসাহী চরম বামপন্থীদের মতবাদের সমর্থক, পার্টি মেম্বার না হলেও তাদের দলের একজন বড় ভরসা!
সুলতা বললে—কংগ্রেসের কথা বললে না?
সুরেশ্বর বললে—তাও বলেছি, অতুলেশ্বরের কথা! তাছাড়া রাজা, জমিদার এরা তো সবাই এখন কংগ্রেসের দলে। কয়েকজন জোতদার অন্তত একজন মহারাজকুমার কম্যুনিস্ট পার্টিতে আছে। তোমাদের দল খুঁজলে গোপনে আমিষভোজী দু-চারজন মিলবে। কিন্তু ও কথা থাক। আমার জবানবন্দী দিয়ে যাই। তুমি শুনে যাও। সন্দেহ হলে প্রশ্ন করে ঘটনাকে পরিষ্কার করে নিও। তার বেশী অধিকার নিলে তোমার পক্ষেও সেটা ট্রেসপাস করা হবে।
সুলতা হেসে বললে—বল।
সুরেশ্বর বললে—ঠিক সেই সময়েই আর্দালী এসে সেলাম করে দাঁড়িয়েছিল। বীরেশ্বর রায় তার দিকে মুখ তুলে তাকাতেই সে আবার সেলাম করে বলেছিল—ছেদী সিং আসিয়েসে বানারসসে!
—ছেদী সিং! চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন বীরেশ্বর রায়। ছেদী সিংকে তিনি দু বছর আগে কাশী পাঠিয়েছিলেন, ভবানী কাশীতে বিমলাকান্তের বাড়ীতে আছে কিনা জানতে পাঠিয়ে ছিলেন। কাশীতে যদি বিমলাকান্তের বাড়ীতে সে থাকে তবে তার সঙ্গে বিমলাকান্তের সম্পর্ক কি তাই জানতে চেয়েছিলেন। রাজা রাধাকান্ত দেব বলেছিলেন, বিমলাকান্ত তাঁকে তাঁর এক ভগ্নীর কথা বলেছিলেন। তাঁর সন্দেহ হয়েছিল—তার এ ভগ্নী ভবানী ছাড়া আর কেউ নয়। ছেদী সিং ছাড়া আর কাউকে এ কাজের ভার দিতে পারেন নি। বিশ্বাসী ছেদী তাঁর বাপের কাছে বাচ্চা চাকর ছিল, তারপর পনেরো-ষোল বছর বয়সে সে তাঁর চাকর হয়েছিল। তাঁর যৌবনে সে তার দেহরক্ষীর মত ছিল। তাঁর সঙ্গে ছায়ার মত ফিরত। ছেদী এখন বৃদ্ধ। তাকে পেন্সন দিয়ে কলকাতার বাড়ীতে রেখেছিলেন। ছেদী যখন কাশী যায়, তখন বিদ্রোহ সবে শুরু হয়েছে। সে যাবার পর বিদ্রোহের আগুন জ্বলল। জ্বলল গোটা উত্তর ভারত জুড়ে। কাশীতেও বিদ্রোহের আগুন জ্বলেছিল। বিদ্রোহে ইংরেজের ক্ষতি সামান্যই হয়েছে। কিন্তু তার প্রতিশোধে ইংরেজ করেছে সেখানে বীভৎস নরমেধ যজ্ঞ। দশ-বারো বছরের ছেলেদের গুলী করে মেরেছে, মানুষকে ফাঁসি দিয়ে ঝুলিয়ে রেখেছে গাছের ডালে। আগুন জ্বালিয়ে হিন্দুস্থানীদের পাড়ার পর পাড়া পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে।
বিহারে আরায় কুমার সিংহের অধীনে বিদ্রোহ হয়েছিল। আরা থেকে সাসারাম পর্যন্ত তিনি কোম্পানীর গোরাদের জীবন দুর্বহ করে শেষ পর্যন্ত ইংরেজের গুলীতে মারা গেছেন। সেখানেও ইংরেজ তার প্রতিহিংসার আগুনে ছারখার করে দিয়েছে সমস্ত কিছু।
এর মধ্যে ছেদী বেঁচে আবার ফিরে আসবে এ প্রত্যাশা বীরেশ্বর রায় করেন নি। বিমলাকান্ত কমলাকান্ত বেঁচে আছে, এ খবর অবশ্য পেয়েছেন। ৫৮ সালের প্রথমেই মিউটিনির ঝড় শাস্ত হয়ে আসছে তখন; তখন চারিদিকে শুধু বিচারের নামে ফাঁসি চলছে। সেই সময় বিমলাকান্ত চিঠি লিখেছিলেন—রামব্রহ্ম ন্যায়রত্নকে লিখেছিলেন।
“শ্রীচরণাম্বুজেষু, অশেষ ভক্তিপূর্বক নিবেদনমেতং, পরে লিখি যে, এই নিদারুণ সঙ্কটপূর্ণ- কালে সকল মানবই বিদেশস্থ আপনাপন স্নেহাস্পদ ও আত্মীয়বর্গ সম্পর্কে উদ্বেগ অনুভব করিতেছেন। সংবাদ না প্রাপ্ত হইলে সকলেই চিন্তিত হইয়া ধারণা করিতেছেন যে, তাঁহারা হয়তো আর জীবিত নাই। এমন এক মন্বন্তরায়—ইহা স্বাভাবিক। সেই কারণে আপনাদিগের জ্ঞাতার্থে নিবেদন যে, আমাদিগের জন্য চিন্তা করিবেন না। কমলাকান্তসহ আমি শ্রীশ্রীকালী মাতা ও শ্রীশ্রীনারায়ণের অনুগ্রহে নিরাপদ কুশলে রহিয়াছি। বড়ই দুর্যোগ এবং দুঃসময় অতীত হইল। বর্তমানে অত্রস্থ স্থানে ক্রমশঃ শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়া আসিতেছে। কীর্তিহাট ত্যাগ করিয়া আসিবার পর হইতে এতাবৎকাল পর্যন্ত কোন পত্রাদিই আমি লিখি নাই। তাহার কারণ, মনে মনে ইহাই ভাবিয়াছি যে, পত্র আদানপ্রদানে শ্রীযুক্ত বীরেশ্বরভায়া আপনাদের উপর ক্রুদ্ধ হইবেন। বড়ই কষ্ট অনুভব করি কিন্তু ইহা যখন আমার উপর দৈবরোষের ফল, তখন ইহা লইয়া পরিতাপ করিয়া কি ফল?
যাহা হউক, আমি বুঝিয়াছি, আমি দুরে থাকিলেই মঙ্গল হইবে। তাহাতে আমিও শান্তিতে আছি। এখানে আসিয়া আমি একটি কর্ম গ্রহণ করিয়াছি। আদালতে দেশীয় ভাষা হইতে ইংরাজাতে অনুবাদকের পদ প্রাপ্ত হইয়া ভালই আছি। শ্রীমান কমলাকান্তও যথারীতি অধ্যয়নাদি করিতেছে।
শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর ভ্রাতৃজীবনকেও কর্তব্যবোধে একখানি পত্র লিখিলাম, তদীয় কলিকাতাস্থ বাসভবনের ঠিকানায়। তিনি প্রত্যুত্তর দিবেন কিনা জানি না। সম্ভবতঃ দিবেন না।
পরিশেষে আপনাদের নিকট নিবেদন—আপনারা তাহাকে অনুরোধ করিয়া সংসারী করুন। এত বড় রায়বংশ, তাহার একমাত্র উত্তরাধিকারী কমলাকান্ত। কমলাকান্তের উপর শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর রায়বাবু প্রসন্ন নহেন। এক্ষেত্রে মদীয় বিবেচনায় তিনি বিবাহ করিয়া সংসারী হইলে পুত্র-কন্যাদি জন্মিলে তাঁহার মঙ্গল হইবে। তাঁহাকে বলিবেন, আমি পত্রেও তাঁহাকে লিখিয়াছি যে, কীর্তিহাট হইতে আসিবার কালীন যে অর্থ ও অলঙ্কারাদি পাইয়াছিলাম কপর্দকও ব্যয় করি নাই। তাহা সবই মজুদ আছে এবং তাহাকে সামান্য সামান্য লগ্নী ব্যবসায়ে বৃদ্ধিও করিয়াছি। তদুপরি বর্তমানে কর্ম করিয়া যাহা উপার্জন করিতেছি, তাহাই লইয়া কমলাকান্ত সন্তুষ্ট থাকিবে। এবং কমলাকান্ত অধ্যয়নে কৃতী হইয়া উঠিতেছে। সম্প্রতি নব-প্রবর্তিত বি-এ পরীক্ষা দিবে। পাশও করিবে। ইচ্ছা করিলে সে কোন উত্তম সরকারী চাকুরিও পাইতে পারে। আইন অধ্যয়ন করিয়া উকীলও হইতে পারিবে। তাহাকে আমি এখন হইতেই বুঝিয়াছি। সে ভবিষ্যতে কীর্তিহাট সম্পত্তির কোন অংশই দাবী করিবে না।
আপনকাদের কুশল প্রাপ্ত হইলে সুখী হইব। আপনি এবং পূজনীয় শ্রীগিরীন্দ্র আচার্য খুড়ামহাশয়কে মদীয় সভক্তি প্রণাম জানাইতেছি।
অধিক আর কি। ইতি—
প্ৰণত
শ্রীবিমলাকান্ত দেবশর্মা (ভট্টাচার্য)
পত্রখানা রামব্রহ্ম ঠাকুর তাঁকে দেখিয়েছিলেন। তিনি পড়ে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেছিলেন।
সুরেশ্বর বললে-জান সুলতা, এই চিঠিখানা পড়ে সেদিন বার বার আমার ভ্রূ কুঁচকে উঠেছিল। মনে মনে কল্পনা করতে চেয়েছিলাম—বীরেশ্বর রায় চিঠিখানা পড়ে সেদিন কি করেছিলেন!
সবুজরঙের ডিম্বাকৃতি স্ট্যাম্পের মাঝখানে সাদা রঙের কুইন ভিক্টোরিয়ার ছবিওয়ালা ছোট আকারের পুরনো খামটা তুলে ধরলে সুরেশ্বর। খামখানার দিকে তাকিয়ে দেখতে দেখতেই বললে—অনুমান করেছিলাম, বীরেশ্বর রায়ের মনের মধ্যে সংশয়-সন্দেহ বোধহয় আরও কুটিল হয়ে উঠেছিল। প্রকারান্তরে বিমলাকান্ত লিখেছে যে, রায়বংশের একবিন্দু রক্তের বা শুক্রের সম্পর্ক যখন কমলাকান্তের সঙ্গে নেই, তখন রায়বংশের সম্পত্তিই বা দাবী করবে কেন?
তিনি অর্থাৎ বীরেশ্বর রায় নিশ্চয়ই রামব্রহ্ম ন্যায়রত্নের চিঠিখানা রেখে বলেছিলেন, চিঠিখানা থাক আমার কাছে। আপনি এখন আসুন।
রামব্রহ্ম ন্যায়রত্নকে বিদায় করে ঘরে গিয়ে মদ্যপান করে তুচ্ছ কোন কারণে রাগে অন্ধ হয়ে সারাটা দিন চীৎকার করেছিলেন। অথবা কাঁসাইয়ের দহে কুমীর বা ওপারের জঙ্গলে ভালুক শিকার করতে যেতেন। তখন কাঁসাইয়ের দহটায় কুমীর থাকত। জঙ্গলেও ভালুক ছিল। মধ্যে মধ্যে বাঘও আসত।
আজ এতদিন পর ছেদী সিং ফিরে এসেছে শুনে বীরেশ্বর রায় চমকে উঠলেন। ছেদী সিং! ছেদী এতদিন পর ফিরেছে? সে বেঁচে আছে? তিনি ভেবেছিলেন, ছেদী বেঁচে নেই। বেঁচে থাকলে ছেদী ফিরবেই-এ বিশ্বাস তাঁর ছিল। কিন্তু দীর্ঘকাল চলে গেল এবং তার মধ্যে মিউটিনির মতো এমন একটা কাল গেল বলে ভেবেছিলেন, ছেদী নেই। ছেদী ফিরে এসেছে এবং যখন এসেছে, তখন ভবানীর খবর তার কাছে পাবেন—এই ধারণাটা বিদ্যুচ্চমকের মত চমকে উঠল।
তিনি আর্দালীকে বললেন—নিয়ে এস তাকে। আর্দালী চলে গেল। কিন্তু তার তর সইল না, নিজেই উঠে বাইরে বেরিয়ে এলেন। আসবার সময় গিরীন্দ্র আচার্য ম্যানেজার-কাকাকে এবং নায়েবকে বললেন, ওবেলা, বাকি কথা ওবেলা হবে। ছেদী এসেছে। ওবেলা।
গিরীন্দ্র আচার্য বোধহয় বিস্মিত হননি। তিনি ছেদীকে চেনেন। পুরনো লোকটির প্রতি বীরেশ্বর রায়ের মমতার কথাও জানেন।
বারান্দার একধারে ছেদী একটা লাঠির উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিল এক পায়ে। আর একখানা পা তার খাটো হয়ে শূন্যে উঠে আছে, শুধু তাই নয়, একটা শুকনো বাঁকা গাছের ডালের মত বেঁকে গেছে।
লাঠি ধরেই ছেদী ঝুঁকে সেলাম করে বললে, হুজুর, গরীবপরবর, আমার ফিরতে বহুৎ দেরী হয়ে গেছে। কসুর মাফ্ কিয়া যায় মালিক। আমি ইচ্ছে করে দেরী করিনি। এহি পায়ের কো লিয়ে দেরী হয়ে গেল।
বীরেশ্বর রায় জিজ্ঞাসা করলেন, কি হয়েছিল পায়ে?—গুলী?
অনুমান করতে কষ্ট ছিল না। বেনারস। মিউটিনি। কর্নেল নীলের নিষ্ঠুর প্রতিশোধ ব্যবস্থা। সবই রায় জানতেন।
—হ্যাঁ হুজুর, গোলী! কলেজায় কি মাথায় বিধল না। বিঁধল পায়ে। নসীব!
পিছন থেকে শিউরে গিরীন্দ্র আচার্য বলে উঠেছিলেন- অসুর। বেটারা অসুর। ওদের সঙ্গে মানুষ পারে!
বীরেশ্বর রায় ছেদীকে বলেছিলেন—তার জন্য আপসোস করো না ছেদী। বেঁচেছ, জীউ পরমাত্মা বেঁচেছেন, সে বিশ্বনাথের কৃপা। ভাবনা কি? আমি তোমার সারা জিন্দগীর ভার নিলাম। কিছু ভেবো না। তোমার বাড়ীর সব বেটা-বহু-পোতা-নাতি এরা—
ছেদী হাতের লাঠিটা শক্ত করে ধরলে। যেন বারদুই টাল খেলে। কিছু বলতে গিয়েও পারলে না। থর থর করে কাঁপতে লাগল দুটি ঠোঁট। চোখ থেকে বেরিয়ে এল জলের ধারা।
গিরীন্দ্র আচার্য শঙ্কিত বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন- ছেদী?
বীরেশ্বর বললেন—বুঝতে পারছেন না, মিউটিনির আগুনে সর্বনাশ হয়ে গেছে ছেদীর। কাশীতে নির্বিচারে গুলী করে মেরেছে গোরারা। দশ-বারো বছরের ছেলেরা তারা কি বোঝে, তারা মিউটিনি খেলা খেলছিল। একদল সিপাহী সেজে চেঁচাচ্ছিল। তাদের ধরে এনে কোর্ট মার্শাল করে সবগুলোকে।
ছেদী সিং এতক্ষণে বললে,—হামার তিনো বেটাকে হুজুর গাছের ডালমে ফাঁসী লঙ্কা দিলে। তামাম গাঁওমে আগুন লাগায় দিলো। ব্যস সব—
টপ টপ করে তার চোখ থেকে জল ঝরতে লাগল।
—তা তোরা ওই ভিমরুলের চাকে খোঁচা দিতে গেলি কেন বাবা? গিরীন্দ্র আচার্য বললেন—ওরে কলিশেষে ওদের রাজত্ব রে; একছত্র। বিধির বিধানের বিরুদ্ধে, আঃ!
বীরেশ্বর বললেন-কি করবে বল? এসেছ, বেশ করেছ। ভাল করেছ। তোমার সব ভার আমি নেব ছেদী। তুমি বাঁচলে কি করে তাই ভাবছি আমি। তোমার পায়ে গুলী লাগল, ওরা তবু তোমাকে ছেড়ে দিলে, ফাঁসী লটকালে না, এই আশ্চর্য।
গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ছেদী বললে—হামাদের জামাইবাবু বিমলাকান্তবাবু হামাকে বাঁচাইলেন হুজুর, উনার বাড়ীমে সে রোজ আসিয়েছিলাম। উনকে হিয়া শুনলাম কি গোরালোক- বীরেশ্বর রায় বাধা দিলেন তাকে।—শুনব ছেদী সিং, ভিতরে এস। বলে ভিতরে চলে গেলেন তিনি।
লাঠিতে ভর দিয়ে একপায়েই সে অনেকটা যেন লাফিয়ে চলার মত ভঙ্গিতে এসে ঘরে ঢুকল। রায় আর্দালীকে বললেন—কাউকে আসতে দিয়ো না। দরজাটা বন্ধ করে দাও।
—তুমি বিমলাবাবুর মোকাম গিয়েছিলে ছেদী?
—হ্যাঁ হুজুর। আপনে ভেজলেন হামাকে, ওহি কাম লিয়ে গেলম, জরুর গিয়েছিলাম হুজুর।
—সে? তাকে দেখতে পাওনি?
ঘাড় নাড়লে ছেদী —না।
—মিথ্যে কথা ছেদী। বিমলাকান্তবাবু তোমার জান বাঁচিয়েছেন বলছ।
উপরের দিকে হাত বাড়িয়ে একটু মুখ তুলে ছেদী ছাদের দিকে তাকিয়ে বললে—বিশ্বনাথজীর নাম সে বলছি হুজুর–ঝুট্ বাত হম্ কভি বলবে না—আপনা সামনে। কভি না!
ছেদীর মুখে সে কথা খোদাই করা ছিল। বীরেশ্বর তার মুখের দিকে তাকিয়ে শুধু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেছিলেন। চেয়ারের উপর বসেছিলেন, মাথাটা ঠেসানের উপর হেলিয়ে দিয়েছিলেন হতাশায়।
ছেদী বলেছিল—হুজুর!
—যাও তুমি এখন—। বলেই আবার বলেছিলেন—না। দাঁড়াও। তার কোন খবরও পাওনি বিমলাবাবুর কাছে?
—হাঁ হুজুর, সো খবর মিলিয়েসে হুজুর। সো খবর হমি আনিয়েছি।
সোজা হয়ে বসে বীরেশ্বর রায় বলেছিলেন—কোথায়—ছেদী সিং?
—বানারসমে হি হুজুর।
—বানারসমে? তবে যে তুমি বললে—
—হুজুর, মাঈজীকে বিমলাবাবুর কোঠীমে হমি নেহি দেখা হুজুর। মাঈজী হুঁয়া থাকতেন না। থাকেন না। হমি কমসে কম বিশ রোজ বিমলাকান্ত হুজুরকে কোঠীমে গিয়েসি হুজুর- কভি নেহি দেখা। কভি নেহি। বহুরাণীজী দেওকন্যা হ্যায় হুজুর, সতীমাঈকী-মাফিক তপস্যা করতি হ্যায়। বিশ্বনাথজীকে মন্দির যানেওয়ালী গলিমে উনকি সাথ হামরা পহেলা রোজ মুলাকাত হুয়া। বিমলাকান্ত হুজুর উনহি কহলেন—ছেদী, তোমার বহুরাণী যোগিনী বন গিয়েছেন। কাশীমে হি উনি আছেন। উনকি বাপকে সাথ রহতি। লেকিন হামারা পাশসে উনহি কসম কি বাত লিয়েছেন, কি উনকি ঠিকানা কোঈকো হম নেহি দেগা।
ছেদী সিং বলে গেল, বীরেশ্বর রায় স্তব্ধ হয়ে শুনে গেলেন।
প্রথম দিন দুপুরবেলা গিয়ে বাড়ীতে সে বিমলাকান্তকে দেখতে পায়নি। কিন্তু বাড়ীর ছাদে শাড়ী শুকুতে দেখে সে ভেবেছিল, বহুমায়ী এখানেই আছেন। ছেদী সিং জানত বীরেশ্বর রায়ের সন্দেহের কথা। মন তার ঘৃণায়, রাগে ভরে গিয়েছিল। নোকর এসে যখন বলেছিল—বাবুজী ঘরমে নেহি হ্যায়, কছহরী গিয়া।
ছেদী বলেছিল—মাঈজীকি কহো কি কীরতিহাট সে ছেদী সিং ভেট মাংতা।
নোকরের কথা শুনে তিনি বলেছিলেন—কে ছেদী সিং আমি তো জানি না।
কথাটা ছেদী চাকরের পিছন পিছন গিয়ে অন্দরের দরজার এধারে দাঁড়িয়ে শুনে আর অপেক্ষা করেনি, জোর করে ঘরে ঢুকে বলেছিল—কি মাঈজী, ছেদী সিংকে আপনি চিনছে না? আঁঃ! কিন্তু কথা সে শেষ করতে পারেনি। সত্যই তিনি অপরিচিতা। একটি সুন্দরী যুবতী, তিনি বহু বটেন কিন্তু বহুমায়ীজী নন।
সে অপ্রতিভ হয়ে মাফ চেয়ে বলেছিল—কসুর হয়েছে মা, কসুর হয়েছে। বহুত কসুর হয়েছে আমার। আমাকে মাফ কর।
তিনি হেসে বলেছিলেন-বুঝেছি বাবা, তুমি কীর্তিহাটের বহুমায়ী, এখানকার সতীমায়ীকে খুঁজতে এসেছ। কিন্তু তিনি তো এখানে থাকেন না বাবা। তিনি—। একটু থেমে ভেবে নিয়ে বলেছিলেন-সে তো আমি বলতে পারব না। কাশীতে তাঁকে লোকে সতীমাঈ বলে। তাঁর খোঁজ করে দেখো। আর বাবুর সঙ্গে যদি দেখা করবে তো বিকেলে আসতে হবে। বাবুজী কাছারীতে কাম করেন। এখন সিপাহী লোক নিয়ে বহুৎ গোলমাল, তার জন্যেও তিনি খুব ব্যস্ত।
ছেদী জিজ্ঞাসা করেছিল -আপনি? আপনি কে মাঈজী?
মাঈজী হেসেছিলেন এবং একটু ঘোমটা টেনে বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। নোকরটা বলেছিল- তুমি তো আচ্ছা বেতরিবৎ আদমী। মাঈজী কে? মাঈজী এ-মোকামের মাঈজী! বাবুজীর স্ত্রী।
অবাক হয়ে ছেদী তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেছিল। মাঈজী হেসে বলেছিলেন—হ্যাঁ বাবা। তুমি অবাক হচ্ছ, তা হবার কথা। তোমরা জানবে কি করে? কাশীতে এসে বাবুজীর সঙ্গে আমার সাদী হয়েছে। ওই সতীমায়ী, তোমাদের বহুরাণীই বাবুকে সাদী করিয়েছেন। আমি বুঝতে পারছি তোমার মন। তা বস না তুমি। বিকেলে বাবু আসবেন। তাঁর কাছে সব শুনবে। থাক। রামলাল, বাইরে ওই তোমার কামরায় ওকে বসতে দাও।
বিকেলবেলা চোগাচাপকান পরে বিমলাকান্ত আপিস থেকে ফিরে ছেদী সিংকে দেখে সমাদর করে বলেছিলেন—ছেদী! তুমি! দেশ এসেছ? না, তোমাদের বহুরাণীজীর খোঁজে এসেছ? বাড়ীর ভিতরে ঢুকে পড়েছিলে, শুনলাম?
লজ্জিত হয়ে ছেদী বলেছিল—হ্যাঁ জামাইবাবু, আমার বহুৎ কসুর হোয়ে গইল হুজুর। আমি ভাবিয়েছিলাম—
—হ্যাঁ। তোমাদের বহুরাণীজী এখানে থাকেন—।
একটু চুপ করে থেকে বলেছিলেন, না, ছেদী সিং। তিনি, তোমাদের বহুরাণী সাক্ষাৎ দেবী। এখানে তাঁকে লোকে সতীমায়ী বলে। তিনি এখানে কেন থাকবেন বল? তিনি তাঁর বাবার সঙ্গে থাকেন। আমি তাঁর পতা জানি। কিন্তু আমাকে তিনি কসম খাইয়েছেন, তাঁর পতা আমি কাউকে বলতে পাব না। বিশ্বনাথজীর সামনে আমাকে বলিয়ে নিয়েছেন।
ছেদী সিং কি বলবে ভেবে পায়নি। বিমলাকান্তই বলেছিলেন—আমি বুঝতে পারছি ছেদী সিং, তোমাকে বীরাবাবু তার খোঁজেই পাঠিয়েছে। তার ধারণা তোমাদের বহুরাণী এখানেই থাকেন। কিন্তু না, তা নয়। বীরাবাবুকেও আমি দোষ দেব না ছেদী সিং। দোষ তাঁর নয়। তোমাদের বহুরাণীর এই বোধহয় নসীব! রাজরাণী আজ যোগিনী হয়ে গেল। পার্বতীমাঈ যেমন শিবের জন্য যোগিনী হয়েছিলেন, তোমাদের বহুরাণী ঠিক তাই হয়েছেন। তুমি যদি তাঁর খোঁজে এসে থাক, তবে খোঁজ কর। কাশীধামে দিনের ভাগে কেউ তাঁকে দেখে না। রাত্রে কোন কোন দিন বিশ্বনাথজীর আরতির পর যখন সব লোক চলে যায় মন্দির থেকে, তখন অন্নপূর্ণা মাতাজীর মন্দিরের পাশে কালীমায়ের আস্তানা থেকে তাঁকে বের হতে দেখতে পাবে। সঙ্গে থাকেন তার বাপ, নয় কমলাকান্ত বাবুয়া। কমলাকান্ত তাঁর কাছে থাকে। কিন্তু সাবধান ছেদী, তিনি কথা না বললে তুমি তাঁকে দিক করো না, তাহলে পাণ্ডারা তোমাকে মেরে জখম করে দেবে। তবে কবে যে তিনি আসেন, তাঁর কোন ঠিকানা নেই। সে তাঁর আপনা মরজি আর খেয়াল।
ছেদী অবাক হয়ে শুনছিল। এবার বলেছিল-আমাকে যে একবার তাঁর দরশন পেতেই হবে জামাইবাবু। বীরাবাবু যে আমার বাউরা হয়ে যাবে হুজুর।
—কিন্তু সে তো ফিরবে না ছেদী সিং। তার জন্যে সে জোড়াসাঁকোর জগদ্ধাত্রী বহুজীকে পত্র লিখেছেন, আমি জানি। বীরাবাবুর সাদী দিতে লিখেছেন। আমাকেও এই বয়সে আবার বিয়ে করিয়েছেন। তুমি ফিরে যাও। ফেরা তো এখন কঠিন হবে। চারিদিকে সিপাহীরা হাঙ্গামা করছে। আরাতে জগদীশপুরে কুমারসিং দানাপুরের সাহেবান লোককে কেটেছে। তার থেকে চিঠি লেখ—
—না হুজুর। তাঁর দেখা যে আমাকে পেতেই হবে।
—তবে চেষ্টা কর। দেখ।
তিনদিন পর দেখা পেলে ছেদী সিং। তখন মিউটিনির আগুন জ্বলে উঠবে-উঠবে এমন সময়। আজিমগড়ে তখন গোলমাল শুরু হয়েছে। আজিমগড় থেকে কোম্পানী সতের লাখ টাকা বেনারস পাঠাচ্ছিল; আজিমগড়ের দেশী সিপাহীরা টাকাটা আটক করেছিল। কিন্তু সাহেবান লোক জবরদস্তি সে-টাকা শেষ পর্যন্ত পাঠালেন। সেখানে সিপাহীরা ক্ষেপে উঠল। সাহেবরা বিবিলোকের সঙ্গে পল্টনের লাইন ব্যারাকে খেতে বসেছিলেন। গুলী-গোলার আওয়াজ উঠতে লাগল। বাইরে বিগল বাজল। আরম্ভ হয়ে গেল মিউটিনি। আগুন জ্বলল আজিমগড়ে। সিপাহীরা কোয়ার্টার মাস্টারকে গুলী করে মারলে। একদল ঘোড়সওয়ার সিপাহী ঘোড়া ছুটিয়ে এসে পথ থেকে সাত লাখ টাকা লুঠে নিয়ে গেল। টাকা লুঠে নিয়ে সিপাহীরা ছুটেছে ফয়জাবাদের দিকে। খবরটা বেনারসে এসে পৌঁছেছে দুদিন আগে। ছেদী যেদিন বিমলাকান্তের সঙ্গে প্রথম দেখা করে তার পরদিন। সেদিন শহরে গুজব থাকলেও শহর ঠাণ্ডা ছিল। ছেদী সিং সেদিন সন্ধ্যা থেকে বিশ্বনাথের গলিতে অপেক্ষা করেও মাঈজীকে দেখতে পায়নি। গরমের সময় সে এসে দশাশ্বমেধ ঘাটে শুয়েছিল। দ্বিতীয় দিনও পায়নি। সেদিন খবরটা এসেছে। যা এতদিন চাপা কানাকানি ছিল, তা এবার লোকে মুখ ফুটে বলছে। এইবার যাবে ফিরিঙ্গীলোক। যাবার ওয়ক্ত হয়েছে।
তৃতীয় দিন শোনা গেল—দেশী সিপাহীদের বন্দুক-তলোয়ার সব কেড়ে নেবে। সিপাহীর এর চেয়ে অপমান হয় না।
ওদিকে আদালতের নাজির পণ্ডিত গোকুলচাঁদ আর সুরত সিং কাছারীর মধ্যে সাহেবানদের বিবি আর বালবাচ্চাদের নিয়ে গিয়ে তুলছেন। তাঁদের সঙ্গে কাজ করছেন বিমলাকান্ত। তাঁর সময় নাই, অবসর নাই। ছেদী বিমলাকান্তের বাড়ীতেই ছিল। সারাদিন গঙ্গার ঘাটে ঘাটে ফিরত। সন্ধ্যার সময় আসত বিশ্বনাথের মন্দিরে। দাঁড়িয়ে থাকত মন্দিরের দরজা বন্ধ হওয়া পর্যন্ত। খানা গিয়ে পাকিয়ে খেয়ে নিত জামাইবাবুর বাড়ী।
সুরেশ্বর বললে—তুমি জান কিনা জানিনে সুলতা, সেকালে বিহার, ইউ পি-র ব্রাহ্মণ- ছত্রীরা যারা এদেশে আসত, তারা যে কাজই করুক মাইনে নিয়ে, বাঙালীর রান্না তারা খেত না। বাঙালী মাছ খায় বলে তাদের অভিযোগ বহু পুরাতন, তখন আবার নতুন করে অভিযোগ উঠেছে, বাঙালী আধা-কিরিস্তান হয়ে গিয়েছে, তারা বাবুর্চির হাতে খায়, মুরগী খায়, পিঁয়াজ খায়। ছেদী সিং কাশীধামেও বিমলাকান্তের মত নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের বাড়ীতেও খেতো না। সে জাতে ছিল ছত্রী। অর্থাৎ ক্ষত্রিয়।
যাক সেকথা। তৃতীয় দিন, যে-কাশীতে ভূমিকম্প হয় না বলে প্রবাদ আছে, সেই কাশী ওই উত্তাপে ভূমিকম্পের মতই যেন মাথা নাড়া দিলে, সঙ্গে সঙ্গে বড় ভূমিকম্পের সময় মাটির ভিতরে যে একটা চাপা গোঙানী শোনা যায়, তেমনি একটা মানুষের চাপা গর্জন উঠল। সেদিন সন্ধ্যে থেকেই লোকের এখান ওখানে জটলা জমে উঠেছে। ভাঙের দোকানে বিক্রী বেড়েছে। সেদিনও ছেদী ওই অন্নপূর্ণা মন্দিরের দরজার পাশে ঘোরাফেরা করছিল। আরতির কাঁসর-ঘণ্টা থামল। প্রথম প্রহর শেষের নহবৎ থামল; গলিতে লোকজন কমে গেছে, গরু-ষাঁড়গুলি বিশ্রামের জন্য শুয়ে পড়তে শুরু করেছে, বাজারের দোকানদানীতে ঝাঁপ পড়ছে, ছেদী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে হতাশ হয়ে ফিরেই আসবে বলে উঠি-উঠি করছে, হঠাৎ তার কানে এল, ভিতর থেকে কেউ বললে—জয় সতী মায়ীজী কি!
মিষ্ট নারীকণ্ঠে উত্তর কেউ দিলে—জয় শিউ সীমন্তিনী কি!
চমকে উঠল ছেদী। সে উত্তেজনায় উঠে দাঁড়াল। একটু ভেবে নিয়ে সিংদরজাকে সামনে করে গলির উল্টোপাশ ঘেঁষে হাতজোড় করে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।
মশাল হাতে একটা লোক বেরিয়ে এল, তারপর সে যাকে দেখলে, তাকে দেখে তার আর বিস্ময়ের অবধি রইল না। সতেরো আঠারো বছরের এক নওজোয়ান। রূপ তার ছিল, রূপবান নওজোয়ান, বুকের ছাতিও এতখানি, মাথায় যে এরই মধ্যে অনেকের চেয়ে উঁচু হয়ে উঠেছে। কিন্তু তা দেখে ছেদী অভিভূত হয়নি, সে অভিভূত হয়েছে এইজন্যে যে, সে তার চোখ এবং চাউনির মধ্যে, তার নাকের ডগার মধ্যে সে যে নওজোয়ানী কালের বীরাবাবুর চোখ-চাউনি দেখছে। নাকের জগাটা অবিকল সেইরকম।
মশালচীর মশালের আলোয় গলির ভিতর-ঠাঁইটা আলোময় হয়ে উঠেছে। অবাক হয়ে দেখছে সে। তার সেই দৃষ্টি দেখে সেই নওজোয়ান ধমক দিয়ে বলে উঠল—কৌন হ্যায় তুম? এই!
এবার চমকে উঠল সে। গলার আওয়াজের মধ্যে বীরাবাবুর আওয়াজ, কথা বলার ঢঙের মধ্যে অবিকল সেই ঢঙ। ছেদী জবাব দিতে ভুলে গেল। চেয়ে রইল নওজোয়ানের মুখের দিকে, বাবুয়া—সেই কমলাকান্ত বাবুয়া? কি তাজ্জব!
নওজোয়ান দরজার সিঁড়ি থেকে লাফ দিয়ে নেমে এসে একেবারে তার সামনে দাঁড়িয়ে আরও গম্ভীর আওয়াজে বললে-কেয়া মাংতা হ্যায়!
ঠিক সেই মুহূর্তে সিঁড়ির উপর দাঁড়ালেন যিনি, তাকে চিনতে একমুহূর্তও দেরী হল ছেদী সিংয়ের। সাত-আট বছর হয়ে গেল, বহুরাণীজী একদিন রাত্রে কাঁসাইয়ের ঘাটে গায়ের গহনা খুলে রেখে কোথায় হারিয়ে গিয়েছিলেন; সেও এই বর্ষার সময়। ভরা কাঁসাই। ভেসে গিয়েছিলেন। তারপর আজ। এই এত দিন পরেও দেখে চিনতে তার এক লহমা দেরী হল না। তার চোখ নওজোয়ান কমলাকান্তের মুখ ছেড়ে তাঁর দিকে নিবদ্ধ হয়েছে। সে বলতে চাচ্ছে, বহুরাণীজী, মাঈজী। কিন্তু তার আওয়াজ বের হচ্ছে না।
—কমলাকান্ত! কি হল? কে যেন বহুরাণীজীর পিছন থেকে কথা বললেন।
—এই একটা লোক—
—যেতে দাও। চল।
—কে ও? কে? এবার কণ্ঠস্বর সতী-মাঈজীর।
—বহুরাণীমাঈ—! ছেদীর গলা কেঁপে উঠেছিল থরথর করে।
—তুমি ছেদী! ছেদী সিং?
—মাঈজী!
ততক্ষণে লোক জমে গেছে সেখানে। সতীমাঈজী কারুর সঙ্গে কথা বলেন না। তিনি আসেন, জপ করেন, চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ে ধারায় ধারায়। তারপর উঠে চলে যান, কিন্তু আবিষ্টের ভাবটা কাটে না। কখনও কখনও অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকেন। অনেকক্ষণ পর জ্ঞান হয়, তখন তিনি ধীরে ধীরে ওঠেন এবং চলেন কমলাকান্তের পিছনে পিছনে। পিছনে থাকেন তাঁর বৃদ্ধ বাপ। কমলাকান্তের সামনে থাকে মশালচী। শশব্যস্ত হয়ে পথ করে দিয়ে সরে দাঁড়ায় পথের লোক। তিনি কারও সঙ্গে কথা বললে লোক জমবে বইকি। লোকটা কে?
কমলাকান্ত ছেদীর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখতে দেখতেই প্রশ্ন করলে—এই সেই ছেদী সিং, ভালো-মা?
সতীমাঈ বললেন—হ্যাঁ। কিন্তু তুই সর। তিনি সামনে এসে দাঁড়ালেন, ছেদীর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন—ছেদী?
ছেদী ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে বললে—মাঈজী! বহুরাণীজী!
—তোমার বাবু কেমন আছেন ছেদী?
—বাবু? হামারা বীরাবাবু?-তার চোখদুটো যেন এক মুহূর্তে ফেটে গেল। জল বেরিয়ে
এল দরদরধারে।
পিছন থেকে মাঈজীর বাপ, তাকেও চিনতে পেরেছিল ছেদী, তিনি বললেন—বাসায় চল মা। বাসায় চল। পথের মধ্যে কেন এসব কথা?
মাঈজী বলেছিলেন—এস ছেদী।
—ভালো-মা!
—কি রে?
—আমি ও-বাড়ী চললাম বাবার কাছে।
একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মাঈজী বললেন—তাই যা।
বীরেশ্বর রায়ের সামনে বসে সেদিনের বৃত্তান্ত বলতে বলতে ছেদী চোখের জল সামলাতে পারেনি। বার বার সে চোখ মুছছিল।
বীরেশ্বর রায় চুপ করে বসে শুনছিলেন। অকস্মাৎ যেন অধীর হয়ে উঠলেন, বললেন—ছেদী, সে কি বললে বল? কি বললে তোমাকে?
—হুজুর! স্রিফ আপকে বাত! ছেদী, তুমার বাবু কেমন আছেন? বাবুজীর তবিয়ত আচ্ছা আছে? বাবুজী তুমার দারু কি বহুৎ পিচ্ছেন? বাবুজীর মেজাজ কি বহুৎ খারাপ আছে? হামি কি বলব হুজুর! বহুরাণীজীর পাশ কুছ ছাপি নেহি। তপস্যাসে সবকুছ উনকি মালুম আছে হুজুর। দেওকন্যা, সাকসাৎ দেবী হইয়ে গিয়েসেন তপস্যা করকে। হুজুর, সোফি বিবিকী বাত ভি উনকি মালুম হ্যায়। হামার মু দেখলেন আর বলিয়ে দিলেন—আমার খোঁজে আসিয়েসো ছেদী? তুমার বাবু ভেজিয়েসেন? আঁ? হামি কুছ বললাম না হুজুর। ডর লাগলো আমার। দেখলম হুজুর, কেশমে তেল নেহি। সারা বদনমে এক আভরণ নেহি। হাঁতমে শঙ্খ, বাস, আর কুছ নেহি। এক বাস হুজুর। লালপাড় এক শাড়ী। বাস্। হামি কুছু বললম না—মাঈজী থোড়া হাসলেন। কহলেন—হমি জানে ছেদী! তুমি বাবুজীকে হুকুম সে আসিয়েসো। উসকে বাদ পুছলেন আপকে বাত। হমি বোলা—মাঈজী, আপকে লিয়ে হামার বীরাবাবুজীর এমুন হালত্। আপনি ফিরিয়ে চলেন মা! চুপসে বৈঠ রহলেন। থোড়া বাদ কহলেন—নেহি ছেদী, সো হোয় না ছেদী। হামার হুকুম নেহি হ্যায়। একতিয়ার নেহি হ্যায়। কালীমায়ী কি হুকুম নেহি। হুজুর, উনকি আঁখোমে পানি আসিয়ে গেল। থোড়া বাদ কহলেন—শুনো, কাল হম এক খত্ লিখ দেগা, উয়ো খত্ লেকে যাও। বাবুজীকে সবকুছ লিখ দেঙ্গে। তুম যাও, বাবুজীকে দেও। আওর উনকে কহো—ফিন সাদী করনেকো লিয়ে।
—এত্তো মোটো চিঠি হুজুর। তিন রোজ লিখিয়েছিলেন। হামি ওহি মোকামমে ছিলাম। আঁখসে দেখা হুজুর, মাঈজী লিখলেন আর কাঁদলেন। একদফে চিঠি লিখলেন, উ ছিঁড়িয়ে দিলেন। ফিন লিখলেন। ঘরসে নিক্লালেন না। রাতমে কালীবাড়ীমে যাইলেন না। চিঠি লিখা শেষ করকে উনকি বুঢ়া বাপজীকে দিলেন। উনি পড়লেন। বললেন—বেফয়দা তুমি লিখলে মায়ী, রায়বাবু এ-চিঠি ফেক্ দিবেন, ছিঁড়িয়ে দিবেন। মাঈজী কহলেন—নেহি বাপুজী, জরুর পড়বেন। কহলেন—আপনে এখুন সব কথা লিখিয়ে দিন। উতো হমি লিখবে না। উনকি বাপুজী তব আর চিঠি লিখলেন; দোনো চিঠি এক করকে লিফাফা বন্দী করকে হামকে দিলেন, কহলেন—তুম জলদি চলে যাও ছেদী। সিপাহীলোককে সাথ গোরা-সাহেবলোককে লড়াই শুরু হো যায়েগা, তুম চলে যাও।
ওহি চিঠি লিয়ে হমি গেলম জামাইবাবুকে হুঁয়া। জামাইবাবু ভি এক খত্ লিখ দিয়া হিঁয়াকে ঠাকুরমহারাজকে দেনে কো লিয়ে। উ দুনো খত্ লিয়ে হমি হামার ঘর যানেকে লিয়ে—
চিঠি নিয়ে নিজের বাড়ী যাবার জন্যে বেরিয়েছিল ছেদী। হঠাৎ পথে গোলমাল শুনে থমকে দাঁড়িয়েছিল। লোকজন ছুটছিল। গোরাদের সঙ্গে সিপাহীদের হাঙ্গামা বেধেছে। ইংরেজ কাপ্তেন কর্নেল নীলের কড়া হুকুমে সিপাহীদের ক্যান্টনমেন্টের মাঠে ডেকে তাদের অস্ত্র সমর্পণ করতে আদেশ দিয়েছিলেন। সামনে কামান বারুদে ঠেসে তৈরী করে রাখা হয়েছিল সাজিয়ে। বন্দুক বা হাতিয়ার কেড়ে নেওয়ার মত অপমান আর নেই সৈনিকজীবনে। এর চেয়ে মৃত্যু ভাল। এক্ষেত্রে কামানগুলোর মুখের মধ্যে সিপাহীরা দেখতে পেয়েছিল আরও কিছু। সেটা এই গোরাদের বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাস। পলাশীর মাঠ থেকে যত লড়াই লড়ছে তারা হিন্দুস্থানের বুকে, তার প্রায় প্রত্যেকটিতে, তারা ঠিক এই পথে লড়াই ফতে করেছে। তবু তারা প্রথমে মাথা হেঁট করে তাদের হাতিয়ার নামিয়ে রেখেছিল। কিন্তু কাপ্তেনের হুকুমে যখন গোরার দল সিপাহীদের নামিয়ে-রাখা হাতিয়ার দখল করতে এগিয়েছিল, তখন আর তারা স্থির থাকতে পারেনি। তারা লাফ দিয়ে পড়ে পরিত্যক্ত বন্দুক কুড়িয়ে নিয়ে শুরু করেছিল ফায়ারিং। মরতে যখন হবে, তখন লড়াই করেই মরবে। বিদ্রোহই ভাল। কানে তাদের বেজে উঠেছিল নানাসাহেব তাঁতিয়া তোপীর আওয়াজ।
সাধারণ মানুষ ছুটে পালাচ্ছিল। ছেদী তার বাড়ীর পথে পড়েছিল এরই সামনে। এবং কিছু করবার আগেই একটা গুলী এসে লেগেছিল তার পায়ে। পড়ে গিয়েছিল উপুড় হয়ে। রাত্রির অন্ধকার নামছে তখন।
ছেদী বীরেশ্বরবাবুকে বলেছিল- হুজুর, সেই আঁধিয়ারার মধ্যে পা টেনে টেনে এসে পৌঁচেছিলাম গলির মুখে। সেটা জামাইবাবু বিমলাকান্তজীর বাড়ীর গলি। সেখানেই পড়েছিল সে।
—রাত কেতনা ঘড়ি মালুম নহি থা।
কাশীতে সেদিন সন্ধ্যা থেকে নহবৎ বাজেনি। কাঁসর ঘণ্টা যেমন বাজে তেমন করে বাজেনি। বিলকুল সবকুছ যেন বদলে গিয়েছিল সেদিন। এরই মধ্যে দুজন দেশোয়ালী তাকে তার অনুরোধে পৌঁছে দিয়েছিল বিমলাকান্ত জামাইবাবুর মোকাম।
তারপর দু মাহিনা যে কিভাবে তার কেটেছে সে জানে না। বিমলাকান্তজী আর তার নতুন বহুজীর তদারকীতে, কবিরাজজীর দাওয়াই-এ কোনরকমে ভাল হয়ে সে উঠল বটে, কিন্তু তখন তার সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে। তিন বেটার ফাঁসি হয়েছে। ঘর-দোর পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। সে নিজে হয়ে গিয়েছে ল্যাঙড়া। লাঠি ধরে সেই বানারস মুলুক থেকে কলকাতা আসতে তার ক্ষমতা ছিল না।
—হুজুর, আমার মগজ গিয়েছিল খারাপ হয়ে। দিনরাত কেঁদেছি। শেষে মাতাজী আমার খবর পেয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর বাসায়। সেখানেই ছিলাম এতদিন। এতদিন পর। হঠাৎ শুনলাম, কমলাকান্তবাবুরা আসছেন বাঙলামুলুক। সঙ্গে আসছেন মাতাজী।
ছেদী শুনে মাতাজীকে হাতজোড় করে বলেছিল—মাতাজী! এ গরীবকে তুমি নিয়ে চল মাতাজী। আমি আমার হুজুরের কাছে বাহ্ দিয়েছিলাম, জান থাকলে আমি ফিরব। জান আমার আছে। কিন্তু কথার খেলাবীর কসুর দিন দিন পখল হয়ে উঠছে। সে দোনা খত্ আমার বটুয়ার মধ্যে আজও আছে। আমি তাকে দেব। কথার খেলাবীর কসুর থেকে আমি খালাস হয়ে যাব।
চমকে উঠলেন বীরেশ্বর রায়।
—কমলাকান্ত? কমলাকান্ত ভবানী এসেছে? কোথায়?
—কমলাকান্ত বাবুজী আসিয়েসেন বিমলাকান্ত জামাইবাবুর আপনা বাড়ী শ্যামনগর। আর মাঈজী চলিয়ে গেলেন উনার পিতাজীর সাথমে।
—কোথায়? জয়নগরের বাড়ীতে?
—না হুজুর। কোই দুা জাগা—হুঁয়া এক ভারী কালীমন্দিল আছে।
বীরেশ্বর রায় চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন—চিঠি কই। যে চিঠির কথা বলছিলে। ছেদী চিঠি বের করে দিলে। মোটা চিঠিই বটে। কাগজ পুরোনো আর ময়লা হয়ে গেছে।
এই সেই চিঠি সুলতা।
সুরেশ্বর কাগজের বান্ডিলটার রেশমী কাপড়ের আবরণ খুলে বের করলেন পত্রখানি। সে আমলের তুলোট কাগজের মত কাগজ। পিছনের দিকটা ময়লা হয়ে গেছে। চিঠিখানা কপালে ঠেকিয়ে সে সযত্নে চিঠিখানা খুললে। বললে—চিঠিখানা স্বামীকে স্ত্রীর লেখা চিঠি হলেও, গোপন করবার মত প্রেমপত্র নয়। তিনি নিজেই পত্রে লিখেছেন—শোন, প্রথমটা পড়ে শোনাই।
শ্রীচরণাম্বজেষু,
সহস্রকোটি প্রণামপূর্বক নিবেদনমিদং। স্বামীন্! আপনি আমার পরম দেবতা। লক্ষ্মীর নিকট নারায়ণ যন্ত্রপ, সতীর নিকট মহেশ্বর যন্ত্রপ, আমার নিকট আপনিও তদ্রূপ। সীতা যেমন রামের নিকট অগ্নিপরীক্ষা দিয়া প্রমাণ করিয়াছিলেন যে, তিনি রামচন্দ্র ব্যতিরেকে চিন্তায়, কর্মে, দেহে অপর কাহাকেও ভজনা করেন নাই, কামনা করেন নাই, তদ্রূপ পরীক্ষায় প্রাণ বিসর্জন দিতে পারিলে আমি পরম ভাগ্যবতী মনে করিতাম। সেদিন আপনার পদাঘাতে যখন আমার ঠোঁট কাটিয়া গিয়াছিল, তখন আর আমার নিজের জীবনের প্রতি ধিক্কারের অবধি ছিল না। হায়, আমি কি করিলাম, কোন্ অপরাধে আমার অদৃষ্টে এমন ঘটিল, তাহার আর কোনপ্রকার কুলকিনারা করিতে পারি নাই। তথাপি আপনাকে বিশ্বাস করিতে কহিতেছি, আমাদের ইষ্টদেবী জগদম্বা কালীমাতার দিব্য করিয়া কহিতেছি যে, আপনাকে আমি দোষারোপ করিতে পারি নাই। আমি নিজেও ভাবিয়া পাই নাই—কমলাকান্ত ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কেমন করিয়া জামাইবাবুর মত দেখিতে হইল! আপনি পুনরায় মদ্যপান করিতে লাগিলেন, আমি নিজেকে এমত অপরাধিনী ধার্য করিলাম যে, আপনার চরণতলে পতিত হইয়া মিনতিপূর্বক নিষেধ করিতেও সাহসিনী হইলাম না। নিরন্তর তাপিত হইয়াই তুষানলেই দগ্ধ হইতে লাগিলাম। কারণ তখনও পর্যন্ত আমি আমার পূর্ণ পরিচয় জ্ঞাত হই নাই। আমার পালক-পিতা—বলিতে গেলে তাঁহাকেই আমার পিতা বলিয়া জানি, তাঁহার স্ত্রীকেই আমার মাতা বলিয়া জানিয়াছিলাম, শুধু শুনিয়াছিলাম, আমার পিতা সন্ন্যাসী হইয়া গিয়াছেন। তিনি বিখ্যাত তান্ত্রিক সাধক ছিলেন।
আমার পালক-পিতা আপনাকে যতটুকু বলিয়াছিলেন, তাহার অপেক্ষা একটি কথাও অধিক তিনি কোনদিন বলেন নাই। আর বলিতেন—আমার জন্মদাতা তান্ত্রিকসাধক পিতার নাম প্রকাশ করিতে তাঁহার এবং আমার গর্ভধারিণী মাতার নিষেধ আছে। এবং ইহা লইয়া আমি কোনদিন কোন কথা চিন্তাও করি নাই। একটা কথা আরও বলিতেন—পিতৃকুলকে উদ্ধার করিবার জন্যই আমার জন্ম। দেবতার ইচ্ছায় আমার জন্ম। তিনি প্রথম স্থির করিয়াছিলেন আমাকে আজন্ম কুমারী রাখিবেন। যে-কোন অশুদ্ধ পাপমতি আমাকে বিবাহ করিলে তাহার সর্বনাশ হইবে। সেই কারণেই আপনার সঙ্গে বিবাহের পূর্বে তিনি আপনাকে প্রতিজ্ঞা করাইয়াছিলেন —আপনি মদ খাইবেন না। আপনার সহিতও বিবাহ দিতে তাঁহার মত ছিল না। কিন্তু বাসরঘরে আপনার বাজনার সঙ্গে গান গাহিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম। এবং এই প্রস্তাব আপনি করিয়াছেন শুনিয়া আমি আনন্দসাগরে ভাসিয়াছিলাম, আমার জগদ্ধাত্রী সইকে বলিয়াছিলাম—সই, তোর ঠাকুমাকে বল, উনি বাবাকে বলিয়া দিউন—আমি বিবাহ করিব। আমার বাবা বরাবর আমার বাল্যকাল হইতে বলিতেন—ভবানীর বিবাহ দিব না। বারণ আছে। আমার গর্ভধারিণী জননীর কথা মনে নাই, তবে আমি যাঁহাকে মা বলিয়া চিনিয়াছিলাম, তিনিও তাহাই বলিতেন। বলিতেন—ভবানী কুমারী থাকিবে—দেবতার আদেশ। কিন্তু ওই বাসরঘরের ঠাকুমা যখন বাবাকে আমার নাম করিয়া বলিয়াছিলেন যে, কন্যা বিবাহ করিতে চাহিতেছে, তখন তুমি বিবাহ দিবে না কেন, তখন বাবা মত করিয়াছিলেন। এবং আপনাকে আমার যেসব কথা বলিয়াছিলেন ও আপনাকে যে শর্ত করাইয়াছিলেন, সেসব কথা আমাকে বলিয়াছিলেন—আমি প্রথম শুনিয়াছিলাম যে, আমার জন্মদাতা দেবতার অভিশাপে রোষে পড়িয়াছেন, তিনি জীবিত বা মৃত তাহা তিনি জানেন না। কিন্তু তিনি জীবিত থাকিলে অনন্ত দুঃখ এবং মৃত হইলে নরক ভোগ করিতেছেন- আমাকে তপস্যা করিয়া তাঁহাকে শাপমুক্ত করিতে হইবে। ইঁহার অধিক তিনি আমাকে কোন কথা বলেন নাই। বলিয়াছিলেন—তাহা জানিতে চাহিয়ো না। মঙ্গল হইবে না।
তাহার পর কমলাকান্তের জন্ম হইল; দিদি তাহাকে আমার কোল হইতে কাড়িয়া লইলেন। সেসময় বাবা আসিয়াছিলেন। তিনি শুনিয়া বলিয়াছিলেন—হয়তো মা, তোমার উপরেও মাতা রুষ্ট হইলেন। নতুবা এমন হইবে কেন। আমি চুপ করিয়াই ছিলাম, কোন কথা কহিতেও পারি নাই। তাহার পর দিনে দিনে আমার অদৃষ্ট মন্দ হইল, আপনি কমলাকান্তকে দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন, আমার চতুর্দিক আমি অন্ধকার দেখিলাম। তাহার পর এই কাণ্ড ঘটিল। অনেক রাত্রি পর্যন্ত কাঁদিয়া কাঁদিয়া কি মনে হইল—এই খিড়কীর ঘাটের সিঁড়িতে আসিয়া বসিলাম। কাঁদিতে কাঁদিতে সিদ্ধপীঠের দিকে হাতজোড় করিয়া বলিলাম-আমাকে বলিয়া দাও আমি কি করিব? অবশেষে আমার মনই বলিল—তুমি মর। ওই লাথিখাওয়া মুখ আর কাহাকেও দেখাইয়ো না। তখন গহনাগুলি খুলিয়া পুঁটলি বাঁধিয়া ঘাটে রাখিয়া জয় মা বলিয়া ঝাঁপ দিলাম। ভাসিয়া গেলাম। কিন্তু আমার এমনই অদৃষ্ট আমি মরিলাম না। কংসাবতীর প্রবল বন্যাও আমাকে গ্রাস করিল না।
বন্যার স্রোতে ভাসিয়া যাওয়া একখানা ঘরের চালে আসিয়া ঠেকিয়া প্রাণের তাড়নায় হয়তো আমিই সেটাকে চাপিয়া ধরিয়াছিলাম। সেই চালটার সঙ্গে ভাসিয়া আসিয়া লাগিলাম হলদীর একটা বাঁকের চড়ায়। সেই চালের উপর একটা বিষধর গোখুরা সপও ছিল। হতভাগিনীর ভাগ্য, সেও আমাকে দংশন করিল না। আমি নিজে তখন অজ্ঞান, জ্ঞান ছিল না, মৃতবৎ সেই চড়ায় আটকানো চালের সঙ্গে পড়িয়া রহিলাম। ইতিমধ্যে ঝড় থামিয়াছে, প্রভাত হইয়াছে, রোদ দেখা দিয়াছে। হলদীতে তখন ভাটির টান পড়িয়াছে। অনতিদূরের গ্রামের লোকেরা বাহির হইয়াছিল, তাহারা আসিয়া আমাকে তদ্রূপ অবস্থায় দেখিয়া প্রথমে মৃত ভাবিয়াছিল। ভাবিয়াছিল, ওই সর্পদংশনে আমার মৃত্যু ঘটিয়াছে। গ্রামের একজন ওঝা আসিয়া ওই সৰ্পটিকে ধরিয়া পরে আমাকে ধরাধরি করিয়া ডাঙায় তুলিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখে আমার মৃত্যু হইয়াছে কিনা। কিন্তু সপবিষের কোন লক্ষণ প্রাপ্ত হয় না এবং আমার মধ্যে তখনও জীবনের লক্ষণ দেখিতে পায়। তখন তাহারা আমাকে দৈবরক্ষিত বলিয়া অনুমান করে ও যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া বাঁচাইতে চেষ্টা করে, লবণ দিয়া আমার সর্বাঙ্গ চাপা দেয়। অনেকক্ষণ পর আমার জ্ঞান ফেরে। কিন্তু সেইদিনই জ্বরাক্রান্ত হইয়া অজ্ঞান হইয়া পড়ি। আমি জ্ঞানপ্রাপ্ত হইয়া তাহাদিগকে বলিয়াছিলাম যে, আমি ব্রাহ্মণ-কন্যা, দয়া করিয়া তোমরা যেন কোন অখাদ্য-কুখাদ্য খাওয়াইয়ো না। কারণ তাহাদিগের মধ্যে আমি কাহারও গলায় উপবীত দেখি নাই। এবং কয়েকজন মুসলমানকেও দেখিয়াছিলাম। একজন অতি সম্ভ্রান্ত মানী মুসলমান মিঞা টুপি মাথায় একটি মোড়ার উপর বসিয়াছিলেন, তিনি আমাকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাঁহাকে আমি অতিকষ্টে বলিয়াছিলাম, —আপনি আমার পিতার মত, আমি আপনার অভাগিনী কন্যা। আর পরিচয় কি দিব?
সেই মহানুভব মিঞা আমাকে বলিয়াছিলেন—মা, তোমার কোন আশঙ্কার কারণ নাই। তুমি আমাকে পিতা বলিলে, আমিও তোমাকে কন্যাই বলিতেছি। নিশ্চিন্ত থাক। আমরা ধর্মে মুসলমান, কিন্তু আমাদের বংশে যোগসাধন আছে। লোকে আমাদিগকে ঠাকুর বলিয়া থাকে। আমরা মুসলমান হইলেও, কাহাকেও জোর করিয়া কখনও মুসলমান করি নাই।
আমার চক্ষুদ্বয় হইতে জল নির্গত হইল। তাহা দেখিয়া তিনি নিজেই বলিলেন—বুঝিয়াছি মা, এই দুর্যোগে তোমার ঘর ভাঙিয়াছে বন্যার জল ঢুকিয়া ঘর ভাসাইয়া ভাঙিয়া গিয়াছে। চালের উপর উঠিয়াছিলে। চালটা বন্যায় তুফানে ভাসিয়াছে।
তখন আমার একটা কম্প আসিয়াছে, দুরন্ত শীত করিতেছিল, কোন উত্তর দিবার ক্ষমতাও ছিল না এবং কিবা উত্তর দিব—খুঁজিয়াও প্রাপ্ত হই নাই।
তখন সেই সম্ভ্রান্ত মিঞাসাহেব ওই গ্রামেরই এক ব্রাহ্মণের ঘরে আমাকে স্থানান্তরিত করিবার আদেশ দেন। এইখানেই দীর্ঘ একমাস আমি রোগভোগ করি। সে প্রায় অচেতন অবস্থায় কাল কাটিয়াছে। একজন সন্ন্যাসী আমার চিকিৎসা করেন।
রোগ হইতে আরোগ্যলাভ করিবার পর ঠাকুরসাহেব আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—মাঠাকুরাণী, সন্ন্যাসীঠাকুর বলিয়াছেন—তুমি অতি পুণ্যবতী ও ভাগ্যবতী ধর্মপ্রাণা। এক্ষণে তুমি অনেকটা আরোগ্যলাভ করিয়াছ, এতকাল অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলে, তোমার বুকে শ্লেষ্মা জমিয়াছিল, বহুকষ্টেই সন্ন্যাসীর চিকিৎসায় সারিয়াছ, এক্ষণে বল, তোমার কে কোথায় আছেন, তাঁহাদের সংবাদ প্রেরণ করি। তাঁহারা আসিয়া তোমাকে লইয়া যাইবেন।
· আমি আপনার পরিচয় তাঁহাকে দিতে পারি নাই, আমার বাবার পরিচয় দিয়াছিলাম এবং বলিয়াছিলাম—যদি কৃপাপূর্বক কোন বিশ্বাসী লোক দ্বারা আমার লিখিত পত্র তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দেন, তবে তিনি আসিয়া আমাকে লইয়া যাইবেন। এবং আমার পিতাঠাকুরকে পত্র লিখিয়া তাঁহাকে অবিলম্বে আসিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম।
এই ঠাকুর মিঞাসাহেবদের অধীনে এই গ্রামে অনেক দুর্ধর্ষ লোক বসবাস করে। ঠাকুর মিঞামহাশয়েরা তাঁহাদিগকে আশ্রয় দিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে গোয়ান আছে, যে গোয়ানরা নদীতে ডাকাতি করিত তাহারা ইহারাই। আরও অনেক বাগ্দী আছে। তাহারা খুব সাহসী লোক। তাহাদের মধ্যে পিদ্রু গোয়ান এই পত্র লইয়া গিয়াছিল এবং পনের দিনের মধ্যে বাবাকে লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল। বাবা আসিলে আমি তাঁহার পদে কান্দিয়া লুটাইয়া পড়িয়াছিলাম। বাবাও আমার মস্তক বক্ষে ধরিয়া অনেক ক্রন্দন করিয়া বলিয়াছিলেন-আমি ইহা জানিতাম মা, আমি ইহা জানিতাম বলিয়াই তোমার বিবাহ দিতে চাহি নাই। তোমার গর্ভধারিণী তিনি সাক্ষাৎ সতীদেবী ছিলেন, তিনি ইহা আমাকে বলিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন—পিতৃকুলের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত এই কন্যাকে করিতেই হইবে। জগজ্জননীর পূজা-অর্চনা করিয়া কুমারীভাবেই কাল কাটাইবে, ইহার বিবাহ দিবেন না। এবং সেইদিন আমাকে আমার জন্মকথা, সত্য পরিচয় বিশদভাবে প্রকাশ করিয়া বলেন। সমস্ত শুনিয়া আমি স্তম্ভিত হইলাম, অনেক কাঁদিলাম এবং বলিলাম —সেদিন বিবাহের পূর্বে আমাকে এসব কথা বলেন নাই কেন। হায়, তাহা হইলে তো এমত ঘটনা ঘটিত না। আমার যাহা হইত হইত, যাহা হইল হইল, আমি যাঁহাকে বিবাহ করিলাম, যিনি আমার দেবতাতুল্য, তিনি তো এমত যাতনা পাইতেন না।
বাবা কি বলিবেন? দীর্ঘক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন-তোমার প্রাক্তন। আর আমার ভ্রম। আমি ভাবিয়াছিলাম এসব কিছু আদৌ ঘটিবে না। অনেকেই আমরা অনেক কথা বলিয়া থাকি, কিন্তু সেসব কি কখনও ঘটে?
অতঃপর অনেক চিন্তা করিয়া আমার পিতা আমাকে লইয়া আমার দাদা বিমলাকান্ত জামাইবাবুর নিকট আমাকে লইয়া আসেন। এবং তাঁহাকে আমার জন্মবৃত্তান্তের কথা, আমাদের পিতার কথা খুলিয়া বলেন। এবং আমার পিতার বাহুতে যে তাঁহার নামাঙ্কিত রূপার চৌকা তাবিজ ছিল, তাহা ও তাঁহার পরিত্যক্ত তন্ত্রশাস্ত্রের বিধিব্যবস্থা লেখা কাগজ-পত্রাদি, এমন কি বিমলাকান্তদাদার মাতামহের হস্তলিখিত সাধনপদ্ধতির খাতা প্রমাণস্বরূপ প্রদর্শন করেন। দাদা কান্দিয়া আকুল হইলেন। আমার পিতাকে বলিলেন—হায়, এসব কথা আগে বলেন নাই কেন? আপনি জানেন না কি অন্তর্যাতনায় আমি দগ্ধ হইয়া আসিতেছি। আমি বুঝিতে পারিতাম না, কেমন করিয়া আমার সহিত কমলাকান্তের এমন সাদৃশ্য আসিল! একথা যখন আপনি জানিতেন যে, আমি এবং ভবানী বৈমাত্রেয় ভ্রাতা এবং ভগ্নী, তখন একথা শ্রীযুক্ত রায়কেই (অর্থাৎ আপনাকে) বা প্রকাশ করিয়া বলেন নাই কেন? তাহা হইলে তো এমত দুর্ঘটনা ঘটিত না। এক্ষণে চলুন তাঁহার নিকট যাই, সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলি। কিন্তু আমার পিতা বলিয়াছিলেন—না। ইহা প্রকাশ করিতে নিষেধ আছে। ভবানীর মাতা, তিনি আমার ভগ্নীতুল্যা, তাঁহার নিকট আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এবং ইহা প্রকাশ করিলে তোমাদের পিতৃবংশ নরকস্থ হইবেন। এবং তোমার পিতা, তিনি জীবিত কি মৃত আমি জানি না, তাঁহার আর এই অভিশাপ কখনও মোচন হইবে না।
অতঃপর কাশীধামে আমাকে লইয়া আসা স্থির হয়। স্থির হয়—সেখানে আমি সংযম নিয়ম পালনপূর্বক ব্রহ্মচারিণী থাকিয়া স্ত্রী মাতার নিকট দ্বাদশ বর্ষ ব্রত পালন করিব।
তদবিধ কাশীতেই রহিয়াছি, সেই ব্রত পালনই করিতেছি। দ্বাদশ বর্ষ পূর্ণ হইতে আর অল্পদিন বাকী আছে। আমার জন্মদাতা পিতা বোধহয় মৃতই হইবেন। কারণ আমার পিতা কামাখ্যা অঞ্চলে কামাখ্যাদেবীর পাণ্ডাগণের দ্বারা অনেক খোঁজখবর করিয়াছেন, কিন্তু কোন সন্ধানই কেহ প্রাপ্ত হন নাই। দ্বাদশ বর্ষ অন্ত হইলে ভাবিয়াছি দেহত্যাগ করিব। মা-গঙ্গা রহিয়াছেন—পতিতপাবনী তিনি, কাহাকেও বিমুখ করেন না। এবার আর ভ্রম করিব না। এবার হস্তপদ বন্ধন করিয়া আশ্রয় লইব। এবং ব্রত শেষ হইলে ভরসা আছে মহামায়া ও আমাকে যন্ত্রণা দিবার জন্য বাঁচাইবেন না। অত্রসহ আমার বাবাকে বহু অনুরোধ করিয়া আমার পিতার সকল বৃত্তান্ত লিখাইয়া অত্র পত্রের সহিত পাঠাইলাম। দেখিবেন—এ হতভাগিনীর ভাগ্যের কিরূপ দয়ামায়াহীন খেলা। দ্বাদশ বর্ষ গত হয় নাই বলিয়া বাবা লিখিতে চাহিতেছিলেন না। আমি তাঁহাকে বলিলাম—তবে কি আমি আমার পতিদেবতার নিকট অপরাধিনী হইয়া থাকিব? ইহার পূর্বেও এরূপ মনে হইয়াছে, কিন্তু আপনি সোফিয়াকে লইয়া সুখে আছেন ভাবিয়া বাবাকে এমন অনুরোধ করি নাই। আজ ছেদীকে আমার সন্ধানে পাঠাইয়াছেন—দেখিতে পাঠাইয়াছেন আমি কাহার সহিত বাস করি, কিরূপ আমার মতিগতি, আপনি সোফিয়াকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, আজ বুঝিতেছি, কি মনঃপীড়া আপনি হতভাগিনীর জন্য ভোগ করিতেছেন ছেদী স্বচক্ষে সমুদয় দেখিল। আমি কাশীতে আসিয়া অবধি আমার আপন দাদা হইলেও বিমলাকান্ত জামাইবাবুর সহিত পৃথক বাস করিতেছি। আমার ব্রহ্মচারিণী ব্রতে আমি পিতা ও পুত্র ব্যতীত কাহাকেও স্পর্শ করি না। লোকে এখানে আমাকে সতীমাতা বলিয়া থাকে। এবং আমি জোর করিয়া দাদার আবার বিবাহ দিয়াছি।
কমলাকান্ত আপনার মতই জেদী হইয়াছে। যত বড় হইতেছে, তত আপনার সহিত সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ হইতেছে। কণ্ঠস্বর অবিকল আপনার মত ভারী। জোরে কথা কহিলে আপনার গম্ভীর কণ্ঠস্বর মনে করিয়া অনেক সময় চমকিয়া উঠি।
আমার পিতার আকৃতিই সে পাইয়াছে। আমার দাদা, তাহার মাতুল, তিনিও অবিকল তদীয় পিতার মত—তদনুযায়ীই তাঁহার সহিত সাদৃশ্য দেখিতে পাইতেন। কমলাকান্ত আজও তাহার আত্মবৃত্তান্ত জানে না। দ্বাদশ বর্ষের ব্রতের পূর্বে জানাইব না। জানাইতে অত্যন্ত ভয় হয়।
পরিশেষে এই হতভাগিনীর অসংখ্য কোটি প্রণাম জানিবেন। এবং এ দাসীর এই মিনতি- পূর্বক নিবেদন যে, এ মন্দভাগিনীকে ভুলিয়া যাইবেন। আমার পিতার অপরাধ—সে-অপরাধ বাবার পত্রে জ্ঞাত হইবেন। আমার সংসারে স্থান নাই, আমার ইহা প্রাক্তন। আপনি এ দাসীকে বিস্তৃত হইয়া পুনরায় বিবাহাদি করিয়া সংসারধর্ম পালন করিবেন। জীবনে সুখী হইবেন। পত্ৰ শেষ করিতে মন চাহিতেছে না। মনে হইতেছে—আরও অনেক লিখি।
জন্মজন্মান্তরে আবার যেন ভাল ভাগ্য লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া আমার স্বামীন, আমার আরাধ্য দেবতাকেই প্রাপ্ত হই—এই আশীর্বাদ করিবেন।
অধিক আর কি। ইতি—
আপনার চরণাশ্রিত দাসী
একান্ত মন্দভাগিনী
ভবানী দেবী
চিঠিখানা পড়া শেষ করে সুরেশ্বর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল, তারপর রুমালে চোখ মুছে বললে—যখনই চিঠিখানি পড়ি সুলতা, তখনই জল আসে আমার চোখে।
সুলতা চিঠিখানা তার হাত থেকে নিয়ে চিঠিখানি দেখলে। তাকিয়েই রইল চিঠিখানার দিকে।
সুরেশ্বর উঠে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল তার একখানা ছবির কাছে। এখানা সেই ছবি, যে ছবিতে শ্যামাকান্তের মৃত্যু হচ্ছে। এক পাশে বীরেশ্বর রায়, এক পাশে ভবানী দেবী, পায়ের তলায় পিছন ফিরে বিমলাকান্ত, কিন্তু তাঁর মুখের একপাশ দেখা যাচ্ছে। তাতে আলো পড়েছে এবং বোঝা যাচ্ছে দাড়ি-গোঁফ, ঝাঁকড়া চুল, শীর্ণ মুখ, মুখের চামড়া ক্ষত-বিক্ষত, শ্যামাকান্তের সঙ্গে কি আশ্চর্য মিল রয়েছে নাকের এবং কপালের। কাল সুলতা এই ছবিখানার সামনে দাঁড়িয়ে বিস্ময়ের সঙ্গে দেখেছিল ওই সন্ন্যাসীর মুখে ধুনির আলোর দীপ্তি কি আশ্চর্য কৌশলে টেনেছে সুরেশ্বর! যেন খানিকটা অলৌকিকত্বের আভাস এনে দিয়েছে।
সুলতা ভবানী দেবীর লেখা চিঠিখানা টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে। বললে—চমৎকার হাতের লেখা। আর চিঠির মধ্যে অন্তরের আশ্চর্য আকুতি! ভারি দুঃখ হচ্ছে। জান সুরেশ্বর, ভারি দুঃখ হচ্ছে!
সুরেশ্বর ফিরে এসে নিজের আসনে বসে বললে—কিন্তু দুঃখকে তিনি জয় করেছিলেন হার মানেন নি।
—সব কালেই তাই। কিছু মানুষ জন্মায় আশ্চর্য শক্তি নিয়ে, তারা হার মানে না, জেতে। তাদের জয়েই মানুষ জেতার পথে এগিয়ে চলে। সে আমি বলছি না। আমি বলছি—অন্ধ ধর্মবিশ্বাসে এই কষ্ট যারা করেছে, তারা ঠিক পথ ফেলে কত এগিয়ে যেত বল তো।
সুরেশ্বর বললে—ও তর্ক আমি করব না সুলতা। কারণ ভবানী দেবী ছাড়া এর জবাব তোমাকে কেউ দিতে পারেন না। তাঁর বিশ্বাস মিথ্যে, একথা তুমি যেমন নির্ভুল বিশ্বাসে বলছ, তেমনি বিশ্বাসের উপর দাঁড়িয়ে তিনিই পারেন বা পারতেন জবাব দিতে। আমি মাঝখানের মানুষ। তাছাড়া আমি কোন বিচার করিনি এঁদের। আমি দেখেই বা এঁদের সম্পর্কে জেনেই শেষ করেছি। যে অপরাধ তাঁরা নিজে স্বীকার করে গেছেন, তাঁদের উত্তরাধিকারী হিসেবে তার দায় আমি মাথা হেঁট করে বোঝার মতো তুলে নিয়েছি।
দপ্তরটা খুলে সে চিঠিখানা রেখে, আরও একখানা চিঠি খুঁজে বের করলে। এবং টেবিলের উপর রাখলে। আগে বের-করা মহেশচন্দ্র মুখুজ্জে অর্থাৎ ভবানী দেবীর পালকপিতা বা ধর্ম-বাপের চিঠিখানা নিয়ে খুললে। বললে-ভবানী দেবী তাঁর বাবাকে দিয়ে লিখিয়ে- ছিলেন যে চিঠি, এখানা সেই চিঠি। মহেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় শ্যামাকান্তের জীবনের প্রথম দিকটা শ্যামাকান্তের কাছেই শুনেছিলেন। মহেশচন্দ্র ইংরেজী শিখেছিলেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এদেশে প্রথম বন্দোবস্তই বল, আর জবরদস্তি দখলই বল, পেয়েছিল চব্বিশ পরগণা। এবং তারা ব্যবসা এবং জমিন দখলই শুধু করে নি, তার সঙ্গে তারা তাদের সুসভ্য ক্রীশ্চান ধর্মের প্রচারও শুরু করেছিল এই অঞ্চলেই। এখনি তুমি বলছিলে—ভবানী দেবী যদি ধর্মের অন্ধবিশ্বাস থেকে মুক্তি পেতেন, তাহলে কত সুখেরই না হত। কত কল্যাণই না হত। কিন্তু মানুষ ঈশ্বর, ধর্ম বা কোন ইজম মাথায় না করে বিপ্লব, দেশজয়, রাজ্যস্থাপন, এমন কি ব্যবসাতে জিনিসে ভেজাল দিতে পারে না। কালোবাজারেও খেলা খেলতে পারে না। দেশের বহু ধর্মশালা, গোরক্ষিণী সমিতি তার সাক্ষী। অশোক ধর্মবিজয় করেছিলেন বৌদ্ধমতে। মুসলমানেরা এসে শুধু বাদশাহি করেনি, তাদের আল্লাকে এনে হিন্দুদের পুতুল ভেঙে এদেশে বসাতে চেয়েছিলেন। মুসলমানকে হঠাতে যখন ইংরেজ এল, তখন তাদের সঙ্গেও মিশনারীরা এসেছিল, আমাদের খৃষ্ট ভজাতে, বাইবেল পড়াতে, কোট-পেন্টালুন পরাতে, ইংরিজী শেখাতে। চব্বিশ পরগণার অনেক প্রচারক এসে মিশন খুলেছিল। মহেশচন্দ্র এদের কাছে ইংরিজী শিখেছিলেন, তারপর চাকরি পেয়েছিলেন, কিন্তু ক্রীশ্চান হন নি। এও মানেন না, ও-ও মানেন না, এমনিতর মানুষ। সেই চাকরি নিয়ে তিনি গিয়েছিলেন গৌহাটি। ইচ্ছে ছিল, দেশে আর ফিরবেনই না। কারণ দেশের সমাজের তরফ থেকে তাঁকে মিশনারীদের সংস্রবে প্রায় পতিতই করেছিল। নিতান্ত কাঁচাবয়স তখন, বাইশ বা তেইশ। গৌহাটিতে খাসিয়াদের ইংরেজী শেখাবার চাকরি; তার সঙ্গে অসমীয়া এবং বাঙালীদের মধ্যে খৃষ্টমহিমা প্রচার ছিল আর একটা দায়িত্ব।
সেইখানে দেখা হয় শ্যামাকান্তের সঙ্গে। কামাখ্যা পাহাড়ে ওই মন্দিরের এলাকার মধ্যে পাগলের মত ঘোরে, কখনও কাঁদে, কখনও হাসে। লোকে বলে—মহাসাধক!
মহেশচন্দ্র হাজার হলেও হিন্দুর ছেলে; বেলপাতা তুলসীপাতার মাহাত্ম্যে বিশ্বাস না করুন, বেলপাতা তুলসীপাতার রসকে উপেক্ষা করতেন না। অসুখে-বিসুখে খেতেন। আসাম তখন কালাজ্বরের এলাকা। তুলসীপাতা বেলপাতা জ্বরের প্রতিষেধক। সেটা ওখানকার লোকের কাছেই তিনি পেয়েছিলেন। লোকে বলত—এ হল পাগলাবাবার ওষুধ। পাগলাবাবা নিজের হাতে তুলে বেলপাতা বা তুলসীপাতা দেয়, ছেঁচে রস করে খেলে জ্বর সারে। পাগলাবাবার নামডাক খুব কিন্তু লোকজনকে কুৎসিত ভাষায় গালিগালাজ করে।
এইসব শুনে মহেশচন্দ্র তাকে তিরস্কার করতে এবং তার সঙ্গে তর্ক করতেই গিয়েছিলেন প্রথমদিন। সেসময় এই পাগল একটা একতারা বাজিয়ে গান করছিল। যেমন তার কণ্ঠস্বর, তেমনি তার তাল আর মানের উপর অধিকার। সব থেকে বড় কথা গানের আকর্ষণী এবং মানুষকে অভিভূত করার শক্তি! জনকয়েক পাণ্ডা আর যাত্রী পাগলাবাবার গান শুনছিল মন্ত্রমুগ্ধের মত; মহেশচন্দ্রও গিয়ে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে তাদের সঙ্গে গান শুনতে বসে গিয়েছিলেন।
গান শেষ করে যন্ত্রটা রেখে পাগল সাধু কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে বসে থাকতে থাকতে কাউকে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ শুরু করেছিল।
লোকজনেরা কেউ কিছু বলে নি, কিন্তু মহেশচন্দ্র বলেছিল—এই সন্ন্যাসী ওহে! শুনছ! কি বলে তোমাকে, পাগলবাবা? এই পাগলা! এই!
হঠাৎ চোখ মেলে সন্ন্যাসী তাকে দেখে বলেছিল—কি?
—এমন কুবাক্য, অশ্লীল বাক্য বলে গালাগাল করছ কেন?
তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে সাধু হঠাৎ অট্টহাস্য করে উঠেছিল—হা-হা-হা, হা-হা-হা, হা-হা-হা!
মহেশচন্দ্র বলেছিলেন—তুমি সাধু, তুমি সন্ন্যাসী, তোমার কাছে মানুষ ভাল কথা শুনতে চায়। তুমি খারাপ কথা বলছ, এ কি রকম সাধু তুমি?
পাগল খানিকটা ধুনির ছাই মুঠো করে তুলে বলেছিল-খাবি?
—ছাই কেন খাব? তুমি খেতে পার?
—দুর বেটা, ছাই কেন হবে, চিনি। এই দেখ না খাচ্ছি আমি। বলে মুখে খানিকটা পুরে দিয়ে স্বচ্ছন্দে খেয়ে নিয়ে বাকীটা অন্য লোকেদের দিয়ে বলেছিল-খা তো রে, তোরা খেয়ে দেখ তো! দেখিয়ে দে তো ওকে!
সকলেই খেয়ে বলেছিল—চিনি!
সাধু সামান্য অবশিষ্টটুকু এবার তার হাতে দিয়ে বলেছিল—দেখ না রে বেটা, দেখ না! চেখেই দেখ না!
বিস্মিত হয়েছিলেন মহেশচন্দ্র। ছাইয়ের স্বাদ তো নয়! স্বাদ তো চিনির স্বাদই বটে! এতেই আকৃষ্ট হয়েছিলেন মহেশচন্দ্র। এর পর প্রায় নিত্যই যেতেন সাধুর কাছে। এবং ক্রমে ক্রমে সাধুর অন্তরঙ্গও হয়ে উঠেছিলেন। সাধুও যেন তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল।
মধ্যে মধ্যে সাধুর পাগলামি বাড়ত। অহরহ অশ্লীল বাক্যে গালাগাল দিয়ে বেড়াত। যাকেই দিক, সে যে কোন নারী, তাতে সন্দেহের অবকাশই রাখত না পাগল। শালী হারামজাদী শব্দেই তার পরিচয় থাকত। শুধু তাই নয়, তখন আবর্জনা ক্লেদ মেখে দাপাদাপি করত। ভক্ষ্যাভক্ষ্যের বিচার থাকত না।
প্রথমবার যেবার মহেশচন্দ্র সাধুর এই অবস্থা দেখেন, সেবার তাঁর গভীর মমতা হয়েছিল। মমতাবশতঃই তিনি সাধুকে জোর করে ধরে স্নান করিয়ে দিতেন, জোর করেই খাওয়াতেন। সাধু কাঁদতেন হাউ-হাউ করে। তিনি তাঁকে সান্ত্বনা দিতেন। বেশী উগ্র হয়ে উঠলে জোর করে বশ মানাতেন। মহেশচন্দ্র বলশালী মানুষ ছিলেন।
এই এতেই সাধু সেবার কয়েকদিনের মধ্যেই শান্ত হয়েছিলেন। এবং মহেশচন্দ্রকে বলেছিলেন—আমার আর একটি কাজ করবি তুই?
মহেশচন্দ্র—কি বল?
গোড়া থেকেই মহেশচন্দ্র তাকে তুমি বলেছিলেন, আপনি আর বলেননি। সাধুও তাকে বলেছিলেন—আমাকে তুই তুমিই বলিস। গালাগালি সম্বোধন করে বলেছিলেন—তুই বেটা ভাল লোক রে! ভাল লোক।
সেদিন সাধু বলেছিল—আমার উত্তরসাধক হবি তুই? দেখ, আমি তাকে টেনে এনেছি। কাছে কাছে ঘুরতে হয় তাকে। ঘোরে, কিন্তু ধরতে আর পারছি না। কিছুতে না! তাতেই তো রাগ করে তেড়ে ধরতে যাই—গালাগালি করি, কিন্তু এমন যে ধরা যায় না। আসল আসন হচ্ছে না। বুঝলি না!
মহেশচন্দ্র বলেছিলেন, সে আমি পারব না।
—পারলে ভাল হত রে! তোকে আমি সিদ্ধির বিভূতি দিতাম। বুঝলি না!
—উঁ-হু। দেখ—ওতে আমার—
—কি? বিশ্বাস তোর এখনও হয় নি?
—বিশ্বাস নয়, বিশ্বাস আর কি করে না করি! তুমি পার অনেক রকম। কিন্তু ওতে রুচি নেই আমার!
—দুর বেটা! রুচি? রুচি কি রে? রুচি? খুব তো রুচি করে ঘি-ময়দার লুচি করে খাস মিষ্টান্ন খাস। পোলাও খাস। খেয়ে হবার মধ্যে হয় তো রক্ত আর বিষ্ঠা। ওরে বেটা, যা খাবি তাতেই ও দুটো হয় রে। রুচি! বলে হা-হা করে হেসেছিলেন।
—দেখ, যা পারব না, তা বলো না। তা’হলে আর একটি কাজ করবি?
—ভাল লাগলে পারব। বল!
—দেখ, আমার একটি নারায়ণশিলা ছিল। বুঝলি। সৌভাগ্যশিলা। সেটি একজন আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে। বুঝলি! ওই শিলা আমিও একজন বৈষ্ণব সাধুকে মেরে কেড়ে নেবার মতলব করেছিলাম, তা সে বোষ্টুম সন্ন্যাসী দিয়ে দিয়েছিল। তারপর আমার কাছ থেকে একজন, আমাকে তুফানের মত বানে ফেলে দিয়ে কেড়ে নিয়েছে। ভেবেছিল আমি মরে যাব। তা মরি নাই আমি। বেঁচে চলে এসেছি কামাখ্যাতে। বেটা জমিদার। ও মুলুকে আমাকে দেখতে পেলে মেরে ফেলত। তাই এখানে এসেছি, সাধন করব বলে। কিন্তু সেই শিলার পুজো আমি এখান থেকে উদ্দেশে রোজ করি। বুঝলি! কিন্তু হচ্ছে কি জানিস? পূজোতে গোলমাল বাধছে। সেই নুড়িটার পূজো করতে গিয়ে মাগীর পুজো করে বসি। আবার মধ্যে মধ্যে মাগীর পূজোতে সেই নুড়িটার পুজোর মন্তর বলে ফেলি। বেলপাতা দিতে তুলসীপাতা দি। আবার তুলসী দিতে বেলপাতা দি। ওই নারায়ণ পুজোটি তুই আমার হয়ে করে দিবি। হ্যাঁ, দিবি!
—কি সব পাগলের মতো বল, আমার মাথায় ঢোকে না!
—ঢোকে না? তবে সব বলি শোন, তাহলে বুঝবি!
শ্যামাকান্ত মহেশচন্দ্রকে নিজের পরিচয় দিয়ে বলেছিলেন—মাগী আমাকে আচ্ছা ধাপ্পা দিলে সেদিন। বুঝলি! একবারে ষোড়শী যুবতী। মড়া হয়ে ভেসে এল জোয়ারে। টকটকে লালপাড় শাড়ী পরনে, এই চুল একরাশ জলে ভাসছে মাথায় সিঁদুর টকটক করছে। পাড়ের ওপর লোকেরা দাঁড়িয়ে হায় হায় করছে, আঃ, কার ঘর ভেঙে দিয়ে সতীলক্ষ্মী জলে ভাসলো গো! হায় হায় হায় হায়। আমি তখন চিনেছি। ঠোঁটে হাসি দেখতে পেলাম। স্পষ্ট দেখলাম। বুঝলাম এসেছে, আসতে হয়েছে। হ্যাঁ, পড়লাম জলে ঝাঁপিয়ে। হাতীর মত জোয়ার ঠেলে গিয়ে ধরলাম চুলের মুঠোয়। ধরলাম যদি তো ঢেউয়ে ঝাঁপ দিয়ে এসে পড়ল আমার বুকে। ডুবিয়ে মারবার ইচ্ছে, বুঝলি না। মেরে ফেলবে আমাকে। তা আমিও শ্যামাকান্ত, ঠেলে ফেলে দিয়ে চুল ছেড়ে কাপড়ের আঁচল দাঁতে ধরে নিয়ে এলাম টেনে। কিনারায় এসে জলে ভাসিয়ে টানতে টানতে নিয়ে এলাম ক্যাওড়াতলায়। কাঁধে করে তুলে গাছের ডালে বেঁধে রাখলাম। রাত্রিটা ছিল চতুর্দশী, কৃষ্ণপক্ষ। বসব ওই মড়ার উপর আসন করে। হ্যাঁ। তারপর কারণ করতে বসলাম। কারণ আর জপ। সিদ্ধি আর মারে কে?
রাত্রে বসলামও। তারপর—।
ভয়ার্ত হয়ে উঠেছিলেন শ্যামাকান্ত সেদিনের স্মৃতি স্মরণ করে। কিছুক্ষণ ভয়ার্ত দৃষ্টিতে কামাখ্যা পাহাড়ের ওপাশে ব্রহ্মপুত্রের স্রোতের দিকে তাকিয়েছিলেন।
হঠাৎ বললেন—দেখ, মরা মেয়েটার মুখখানা ছিল অবিকল বিমলার মায়ের মত দেখতে। বিমলা আমার ছেলে। বুঝলি। রাত্রে মড়াটা নামিয়ে এনে গণ্ডীটণ্ডী কেটে তার মধ্যে তাকে রেখে মুখের ঢাকাটা খুলে দিয়ে ইষ্টমন্ত্র স্মরণ করে আসন করে বসতে যাব, এমন সময় দেখি কি জানিস? এ তো সে মড়া নয়! এ তো বিমলার মায়ের মুখ নয়! এ যে এ যে—ওরে, দেখি ঠিক যেন আমার মায়ের মুখ। অবিকল রে অবিকল! আর মরা তো নয়, এ যে চোখ খুলে তাকাচ্ছে!
ভয়ে আমি পিছিয়ে গেলাম। পিছিয়ে গিয়ে দাঁড়ালাম, আবার তাকালাম, দেখলাম—না তো! এ তো সেই মুখ! হ্যাঁ! সেই যেমন বানে ভাসবার সময় হাসি দেখেছিলাম, তেমনি হাসছে যেন! যেন ডাকছে, বলছে-এস এস। আসন করে বস, ভয় কি? বুঝলি, কানের কাছে যেন ফিসফিস করে বললে।
ধুনি জ্বেলেছিলাম। ধুনিতে আগুন জ্বলছে। আমি দেখছি। হ্যাঁ, ঠিক সেই। ঠিক। আবার ইষ্ট স্মরণ করে এগিয়ে গেলাম। কিন্তু যত যাই এক পা এক পা এগিয়ে, ততই যেন পাল্টে যায়। স্পষ্ট দেখলাম, কই, সিঁথিতে তো সিঁদুর নাই। বয়স যেন কমে গিয়েছে। ছোট হয়ে গেছে মড়াটা। থমকে দাঁড়ালাম। এ কি? এ কি? এইসময় হঠাৎ হল কি জানিস, দুটো জন্তু- শেয়াল না কি জন্তু—কালো মতো দেখতে, খ্যা খ্যা করে ঝাপটাঝাপটি করতে করতে এসে পড়ল সেই ধুনির ওপরে। বুঝলি! জ্বলন্ত ধুনি নিবে গেল। আর সে কি চিৎকার! খ্যা-খ্যা করতে করতে আওয়াজ যে কি বিকট হয়ে উঠল, কি বলব! চারিদিক অন্ধকারে ঢেকে গিয়েছে তখন, কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। সঙ্গে সঙ্গে বোধহয় হাজার খানেক শেয়াল ডেকে উঠল। হুয়া হুয়া হুয়া হুয়া!
আমার মনে হল, হা-হা-হা-হা করে হাসছে। আমি তখনও দাঁড়িয়ে আছি। বুকের মধ্যে যেন ঢাক পিটছে। নিঃশ্বাস নিচ্ছি, মনে হচ্ছে পচা মড়ার গন্ধে দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এমন সময় মনে হল কে যেন আমার একখানা হাত চেপে ধরলে। কনকনে ঠাণ্ডা একখানা হাত। সমস্ত শরীর চমকে উঠল। আমি চিৎকার করে উঠে হাতখানা ঝাঁকি দিয়ে ছাড়িয়ে নিয়ে ছুটে পালাতে গেলাম। কোথায় পালাব? তখন অমাবস্যার কোটাল ডেকেছে গঙ্গায়, আমি জলে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। জোয়ার যাচ্ছে কালীমন্দিরের দিকে। সেই দিকে ভেসে এসে ধাক্কা খেলাম একটা গাছের শিকড়ে। মনে হল মরে যাব। কিন্তু কোনরকমে আঁকড়ে ধরলাম তার শেকড়টা। আস্তে আস্তে সামলে নিয়ে ওই শেকড়টা ধরে ধরে পাড়ে উঠে আর খাড়া হতে পারলাম না। সেই শিকড়ে মাথা দিয়ে পড়ে রইলাম।
আমার আর কিছু মনে ছিল না। অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। একে শীতকাল, তার উপর সমস্ত রাত্রি ওই জোয়ারে ভেসে এসে গাছের শেকড় ধরে কাদার উপর পড়ে থেকে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম। যখন জ্ঞান হ’ল তখন দেখলাম, এক বৈষ্ণব সাধু একটা গোলপাতার ছাউনি ছোট ঘরের মধ্যে কড়াইয়ে আংরা করে আমাকে তাপ দিচ্ছেন। সাধুর মাথাতে জটা, কপালে বৈষ্ণবদের হরিচন্দনের তিলক। গলাতে মোটা তুলসীকাঠের মালা। আমাকে চোখ মেলতে দেখে বললেন, কেয়া বাবা, আব আচ্ছা মালুম হোতা?
একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে শ্যামাকান্ত মহেশচন্দ্রকে বলেছিলেন–আঃ, মহেশ, এই সাধুর সঙ্গে যদি দেখা না হত! বুঝলি! আঃ!
আবার অনেকক্ষণ চুপ করে ছিলেন শ্যামাকান্ত। সেই সেইকালের কথা মনে পড়েছিল।
সুরেশ্বর মহেশচন্দ্রের চিঠিখানা খুলে ধরে বললে-এইখানটা পড়ে শোনাই তোমাকে সুলতা। বীরেশ্বর রায়কে শ্যামাকান্তের বৃত্তান্ত লিখতে গিয়ে এইখানটায় লিখেছেন—
তুমি মদীয় জামাতা, পুত্রস্থানীয়, তোমাকে অকপটে কহিব যে, হিন্দু ব্রাহ্মণ সন্তান হইয়াও প্রথম বয়সে পাদ্রীদের কাছে ইংরাজী শিখিয়া এইসব সাধনভজনের ক্রিয়াপ্রক্রিয়া ফলাফলের সত্যতা সম্পর্কে আজও সম্যক পূর্ণবিশ্বাসী নহি। শ্যামাকান্ত তদীয় এই সময়কার বৃত্তান্ত কহিতে গিয়া বলিয়াছিলেন—সাধু আমাকে আমার চার জন্মের কথা বলিয়াছিলেন। জন্ম-জন্মান্তরের কথা বিশ্বাস করা আমার পক্ষে শক্ত হইয়াছিল সেদিন। আজও সংশয় আছে, কিন্তু শ্যামাকান্তের সংশয় ছিল না।
শ্যামাকান্ত সেদিন চোখে মেলেছিলেন বটে কিন্তু পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠতে লেগেছিল এক মাস। শ্লেষ্মাদোষে জ্বর হয়েছিল তাঁর। বৈষ্ণব তাঁকে ফেলে দেন নি। তিনিই তাঁর সেবা করে চিকিৎসা করে সুস্থ করে তুলেছিলেন। বরং সেইসময় তাঁকে তিনি বলেছিলেন তাঁর জন্ম- জন্মান্তরের কথা। এক জন্ম নয়, চার জন্মের বৃত্তান্ত। প্রথম জন্মে শ্যামাকান্ত নাকি পিশাচসিদ্ধ হয়েছিলেন। সেই জন্মে নাকি এক মেয়েকে তিনি ভালবেসেছিলেন, কিন্তু সে মেয়ে ছিল বড়ঘরের, তার ধনদৌলত ছিল, আর চার জন্মের আগের শ্যামাকান্তের কিছু ছিল না, গরীব ঘরের ছেলে ছিল সে। এক জমিদার রাজা ঘরের ছেলে সে মেয়েকে বিয়ে করেছিল। চার জন্ম আগের শ্যামাকান্ত সেই দুঃখে ক্ষোভে পিশাচসিদ্ধ হবার সাধনা করেছিল। হয়েছিল সে পিশাচসিদ্ধ। পিশাচকে দিয়ে সে সেই মেয়ের স্বামীকে মেরে ফেলেছিল। কিন্তু সে মেয়েকে সে পায় নি। সে স্বামীর চিতায় পুড়ে মরেছিল। তখন শ্যামাকান্ত সেই পিশাচকে দিয়ে শুরু করেছিল ব্যভিচার-অত্যাচার। শেষে পিশাচই তাকে একদিন বধ করেছিল। দুসরা জনমে নাকি তিনি হয়েছিলেন বড়া ভারী জমিদার। সে ওই পিছলা জনমের ফল। বহুত ভোগ করেছিল। তবু লালসা তার মেটেনি। দেওতার সেবাও করেছিল। তার ফলে তিসরা জনমে হয়েছিল যোগী। বহুৎ খেয়ালী আদমী। রাজা-মহারাজা-বাদশা তাকে খাতির করত, কিন্তু তাতেও তার লালসা মেটেনি। কি হ’ল তার যোগে, যদি সে তামাম দুনিয়ার মালিক না হল! ব্রহ্মচারী ছিল, না হলে যোগ হয় না, কিন্তু তাতেও তার ক্ষোভ ছিল। তাই শেষজীবনে সে শক্তি-সাধনা শুরু করেছিল—সে শক্তির মালিক হবে। এই তার চৌথা জনম। সে তারই জের টানছে। লেকেন–।
শ্যামাকান্ত হেসেছিলেন, লেকেন কি বাবাজী? লেকেন!
—লেকেন, বাবা, ওহি পিশাচটো! উ তুমকো নেহি ছোড়তা!
শ্যামাকান্ত বলেছিলেন—সেই শালাই তাহলে সেদিন রাত্রে আমার সাধন পণ্ড করেছে! ঠিক বলেছ তুমি!
—হাঁ বাবা, পহেলে উসকো ভাগানেকা জরুরৎ হ্যায়।
সন্ন্যাসীকে বড় ভাল লেগেছিল শ্যামাকান্তের। সন্ন্যাসী তাঁকে বলেছিলেন—বাবা, কিছুদিন তুমি শুদ্ধাচারে ক্রিয়া-করম কর। ব্রাহ্মণের ছেলে ব্রাহ্মণের আচারে নিজেকে শুদ্ধ কর। পিশাচ অশুদ্ধ আত্মা, তোমার আত্মা শুদ্ধ হলে সে ভাগবে।
তাই করতে শুরু করেছিলেন শ্যামাকান্ত। ইতিমধ্যে এসেছিল গঙ্গাসাগর স্নানের তিথি। বৈষ্ণব সন্ন্যাসী গঙ্গাসাগর যাবেন বলেই এসেছিলেন কালীঘাট। এখান থেকেই নৌকা-টৌকায় কোনমতে জায়গা করে নেবেন। আরও অনেক সাধু-সন্ন্যাসী আসবে, সঙ্গী জুটে যাবে। আরও কয়েকবার তিনি সাগরতীর্থ গিয়েছেন। শ্যামাকান্তও বলেছিলেন-তিনিও যাবেন তাঁর সঙ্গে।
মহেশচন্দ্রের চিঠিখানা আবার তুলে নিয়ে সুরেশ্বর বললে—সুলতা, মহেশচন্দ্র লিখেছেন- “কিন্তু শ্যামাকান্ত পুণ্যার্জনের জন্য সাগরতীর্থে যাইতে চাহেন নাই। তিনি আমাকে বলিয়া- ছিলেন—ওই বৈষ্ণব সাধুর নিকট এক দুর্লভ নারায়ণশিলা ছিল। ওই শিলাটির অর্চনা তিনি যখন করিতেন, তখন আমি নিরীক্ষণ করিয়া দেখিয়া লক্ষণ হইতে বুঝিয়াছিলাম, এই শিলাকেই বলে সৌভাগ্যশিলা। এ শিলা যাহার নিকটে থাকে, তাহার সৌভাগ্যের অন্ত থাকে না। দরিদ্র রাজা হয়। গৃহী অশোক হয়। এ শিলাকে সহায় করিয়া মানুষ যে সাধনাই করুক, তাহাতে সে নিশ্চিত সিদ্ধিলাভ করে।
শ্যামাকান্ত একদিন সাধুকে প্রশ্ন করেছিলেন-এ শিলাটি কোথায় পেলেন গোসাঁইজী?
সাধু বলেছিলেন—এ শিলা আমি বদ্রীনাথের পথে এক সাধুনির কাছে পেয়েছিলাম।
—এ কি শিলা বাবা! সৌভাগ্যশিলা নয়?
হেসে গোসাঁই বলেছিলেন—সৌভাগ্য কামনা করে অর্চনা করলে এ সৌভাগ্যশিলা। যা চাও, তাই মেলে। ধন-দৌলত, মনস্কামনা পুরণ—সবই দেবেন উনি। আর কিছু না চাইলে উনি দেন পরমধন বাবা, চৈতন্য। উনি আসলে হলেন চৈতন্যশিলা।
—হুঁ।
গোসাঁই বলেছিলেন-ঝুটা বাত আমি আর বলি না বাবা। আমি যখন প্রথম সন্ন্যাসী হই, তখন আমি ভাল আদমী ছিলাম না। চোর ছিলাম।
—চুরি করেছিলেন এই শিলা?
—তা বলতে পার। সন্ন্যাসীর সঙ্গে ঘুরছিলাম কিছুদিন। তাঁর কাছে রোটির ভাবনা হত না। রোটি তিনি দিতেন। মতিও ফিরেছিল। তিনি মরবার সময় আমাকে এই শিলা দিয়ে বলেছিলেন—দেখ বেটা, এই শিলা সাগরসঙ্গম মে বিসর্জন দেনা। হ্যাঁ, তিন দফে হম সাগর- তীরথ গিয়া, ওহি কো লিয়ে, লেকেন দিল নেহি উঠা!
বাবা, গিয়েছি বিসর্জন দিতে, কিন্তু পারি নি, ফিরে নিয়ে এসেছি। তারই জন্য এবারও চলেছি বাবা। এবার ঠিক করেছি নিশ্চয় বিসর্জন দিয়ে আসব।
শ্যামাকান্ত যেতে চেয়েছিলেন ওই শিলাটির লোভে। ওই শিলা পেলে তাঁর মনস্কামনা নিশ্চয় পূর্ণ হবেই হবে।
গঙ্গাসাগরে গিয়ে শ্যামাকান্ত মুহূর্তের জন্য গোস্বামীর সঙ্গ ছাড়েন নি। তিনি ফেলে দিলেই শ্যামাকান্ত ঝাঁপিয়ে পড়ে তুলে নেবেন। কিন্তু বিচিত্র কথা, গোস্বামী রোজ ওই শিলাকে ঝুলিতে পুরে বুকে ঝুলিয়ে নিয়ে স্নান করে এলেন, কিন্তু বিসর্জন দিতে পারলেন না।
শ্যামাকান্ত রোজ জিজ্ঞাসা করেছেন—কই, বিসর্জন দিলেন না গোসাঁই?
গোসাঁই বলতেন—নেহি বাবা। নেই সকা! কিছুতেই পারলাম না। পারছি না, পারব না!
শ্যামাকান্ত মনে মনে হিংস্র হয়ে উঠছিলেন। মনের মধ্যে নানান কুটিল অভিপ্রায় জেগে উঠছিল। কিন্তু এই গোসাঁই তাঁকে সেদিন মৃত্যুর মুখ থেকে বাঁচিয়েছেন। এতটা নিষ্ঠুর, অকৃতজ্ঞ তিনি হতে পারেন নি। কিন্তু মনের মধ্যে দ্বন্দ্বেরও শেষ ছিল না। শেষ ওই গঙ্গাসাগর থেকে ফিরবার আগের দিন রাত্রে শ্যামাকান্ত অস্থির হয়ে উঠেছিলেন—ও শিলাটি তাঁর চাই। সৌভাগ্যশিলা। ওই শিলাই তাঁর জন্মজন্মান্তরের পিশাচকে তাড়াবে, তাঁকে সিদ্ধি দেবে। ওটি তাঁর চাই!
তখন গভীর রাত্রি। মাঘ মাসের প্রথম, সাগরদ্বীপের শীত। বাতাস বইছিল। শ্যামাকান্ত ঘুমুতে পারেন নি, গোস্বামী সাধুর পাশেই শুয়েছিলেন। তিনি এই দ্বন্দ্বের মধ্যে ঘুমুতে না পেরে উঠে বসলেন।
মনের মধ্যে তাঁর কুটিল খেলা চলছে।
উপকার করেছে! ধুত্তোর, কিসের উপকার? আমার মৃত্যু হবার হ’লে ও বাঁচাতে পারত? যে সিদ্ধিতে মরাকে বাঁচানো যায়, তা ওর নেই, ও বেটা পায় নি। তা ছাড়া ওর গুরু ওকে বলেছিল—এ শিলাকে সাগরতীর্থে বিসর্জন দিতে। বেটা চারবার এসে পারল না। এ তো ওর নয়। ওকে যদি—!
পাশে একটা ধুনি জ্বলছিল। শীতের জন্যও বটে, জানোয়ারের জন্যও বটে। সেটাতে কাঠ চাপিয়ে ফুঁ দিয়ে দিয়ে সেটাকে উজ্জ্বল করে তুলছিলেন শ্যামাকান্ত। তারই দীপ্তিতে ঘুমন্ত সাধুকে দেখছিলেন।
কম্বলের বালিশ করে শুয়েছে গোসাঁই। ঝুলিসমেত সৌভাগ্যশিলাটিকে বেটা কম্বলের ভাঁজের মধ্যে পুরে রেখেছে। মাথার গোড়ায় ছোট সিংহাসনে ছোট্ট আধ হাত পরিমাণ উঁচু রাধাকৃষ্ণমূর্তিটি রয়েছে। বেটার ভয় হয়েছে, না হয় কঠিন লোভ ওই শিলার ওপর! রাধাকৃষ্ণমূর্তি চুরি যাক, তা সহ্য হবে। এ শিলা চুরি সইবে না।
ক্রমাগত ধুনিতে ফুঁ দিচ্ছিলেন শ্যামাকান্ত। এবং একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলেন ওই আগুনের দিকে। মধ্যে মধ্যে তাকাচ্ছিলেন সাধুর দিকে। ইচ্ছে হচ্ছিল—
হঠাৎ গোসাঁইয়ের সাড়ায় শ্যামাকান্ত দৃষ্টি ফেরালেন সন্ন্যাসীর দিকে। দেখলেন, গোস্বামী সাধুও তাঁর দিকে তাকিয়ে আছেন।
গোস্বামী সন্ন্যাসী উঠে বসলেন। বললেন—ঘুম আসছে না তোমার?
শ্যামাকান্ত উত্তর দেন নি। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়েই ছিলেন তাঁর দিকে।
গোস্বামী বললেন-ওই শিলাটির জন্যে, না?
শ্যামাকান্ত এবার বলেছিলেন—হ্যাঁ, গোসাঁই। ওটি তোমাকে বিসর্জন দিতেই হবে। তুমি বিসর্জন দেবে—আমি তুলে নোব। ওটিকে আমাকে পেতেই হবে। ওটি আমার চাই গোসাঁই!
—না দিলে?
—না দিলে? প্রশ্নের পুনরুক্তি করে সাধুর চোখে চোখ রেখেই তাকিয়েছিলেন শ্যামাকান্ত, তাঁর পলক পড়েনি। কিন্তু মনে যা হচ্ছিল—তা বলতেও পারেননি।
—জবরদস্তি কেড়ে নেবে?
—তা নেব গোসাঁই! ও আমার চাই!
কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে গোসাঁই বলেছিলেন—তাতে যদি আমার জান নিতে হয় তাও নেবে! নয়?
—তা—
—একবার গাঁজা সাজ বাবা। গাঁজা খাই। তারপর তাই হবে। তাই নাও। ও তোমারই হয়েছে। ওর যা দেবার তা আমাকে ও দিয়েছে। চৈতন্য হয়েছে আমার।
হেসেছিলেন সাধু।
গাঁজা খেয়ে ঝুলিসুদ্ধ থলিটি নিয়ে ভোরবেলা সঙ্গমস্থলে এসে জলে ডুবিয়ে থলির দড়ি শ্যামাকান্তের হাতে দিয়ে বলেছিলেন, নাও, ধর। কিন্তু এরপর তুমি আর আমার সঙ্গে এস না। হ্যাঁ!
—আমার একতারা আর লোটা কম্বল নিতে হবে।
—সে আমি ঝোপড়ীর বাইরে রেখে দিচ্ছি গিয়ে। তুম উঠা লেকে চলে যাও ভাই। ঝোপড়ীর বাইরে লোটা কম্বল আর একতারাটি তুলে নিয়ে পা বাড়াবেন শ্যামাকান্ত, ভিতর থেকে সন্ন্যাসী বললেন—আর এক বাত ভাই!
—কি?—কি?
—এই সাগরতীরথে বাত দাও কি—তুমি তোমার মনস্কামনা সিদ্ধি হলে—ওই শিলাকে এই সঙ্গম তীরথে বিসর্জন দেবে!
—দেব!
সন্ন্যাসী কাঁদছিলেন—তাঁর কথার ভঙ্গি এবং কণ্ঠস্বরের মধ্যে তা প্রকাশ পাচ্ছিল। কথার স্বর কাঁপছিল।
কিন্তু শ্যামাকান্ত তাতে ভ্রূক্ষেপ করেননি। তিনি পেয়েছেন। এবার তিনি পেয়েছেন। এই যে শিলা—সৌভাগ্যশিলা—একে দিতেই হবে—তিনি যা চান। সিদ্ধি তাঁকে দিতেই হবে।
শবাসন হোক বা যে আসন হোক করে বসবার আগে—যন্ত্র আঁকতে হবে। সেই যন্ত্রের মধ্যে বিষ্ণুর স্থান আছে। পূজা আছে। চতুর্দ্বারে বিষ্ণু-শিব-সুর্য-গণেশ
—ওঁ বিষ্ণবে নমঃ শিবায় নমঃ ওঁ সূর্যায় নম গণেশায় নমঃ। তারপর—মহামেঘ প্রভাং দেবীং কৃষ্ণবস্ত্রপিধায়িনীং —।
এবার তিনি পেয়েছেন।
একতারা বাজিয়ে নৌকোয় আসর জমিয়ে রেখে ফিরেছিলেন শ্যামাকান্ত
তাদের কথার মধ্যে এসে ঘরে ঢুকল অর্চনা।
অর্চনার হাতে শালপাতে মোড়া কিছু। সুরেশ্বর কথা বন্ধ করে বললে—আয়। কখন ফিরলি?
—এই তো। গাড়ী থেকে নেমেই উপরে আসছি। রঘু বললে—সুলতাদি এসেছেন—আজ আবার লালবাবু সেই কালকের কথা ফের আরম্ভ করেছে। নাও-মাথাটা নামাও।
—কি? ও কালীঘাট গিয়েছিলি বুঝি!
—হ্যাঁ মায়ের নির্মাল্য।
মাথা হেঁট করলে সুরেশ্বর। মাথায় নির্মাল্য ঠেকিয়ে দিয়ে অৰ্চনা বললে-তোমার হয়ে আমি মাথায় ঠেকালাম সুলতাদি। তোমায় দিতে গেলে তুমি পড়বে অস্বস্তিতে। তোমায় না দিয়েও আমার তাই হচ্ছে।
সুলতা হেসে বললে—আমার কল্যাণটাও তোমার হোক।
—তাই হোক। আচ্ছা আমি চলি–সুরোদা। এখনও চা খাই নি।
—কেন? অতুলের ওখানে যাস নি?
—গিছলাম। কিন্তু সন্ধ্যে করবার সুযোগ পেলাম না, বসলামও না। ভাল লাগল না আমার। যে অতুলকা—মিটিং করতে যাবার সময় কি কোন কাজে যাবার সময় মেজদির হাতে মায়ের পুষ্প মাথায় না ঠেকিয়ে যেত না, সমিতি গড়বার সময় কালীমাকে ধ্যান করত; পুজো করত; সে বলে—পুষ্প-টুষ্পে বিশ্বাস নেই অর্চি, ও আমায় দিসনে। দেবোত্তরের কথায় বললে-শরিকরা ঠিক বলছে জমিদারী সরকার নিচ্ছে, নেওয়া উচিত—ও পাপ থাকা উচিত নয়, কিন্তু যা খাস জমি আছে তা দেবতার নামে থাকার কোন মানে হয় না। ও হল জমিদারীর হাতী ঘোড়া লোক লস্কর না হোক কুলীন ঘরজামাইয়ের সামিল। আলাদা মহল তার পূজক পুরোহিত, বাল্যভোগশীতল-অন্নভোগ! কেন? আমি বললাম-সে কি ছোটকা; তুমি এই কথা বলছ? বললে—বলছি! কারণ ওসব এযুগে অচল। তুই বলিস সুরেশ্বরকে। বলিস আমি বলেছি। দেবোত্তর ক্যানসেল করে দিক। কমপেনসেশনের টাকা শরিকেরা ভাগ করে নিয়ে নতুন করে ব্যবসা-বাণিজ্য করে বাঁচুক। আচ্ছা বলব, বলে আমি উঠে চলে এলাম। জান, ব্রজদা পথে কাঁদলে। বললে—অতুল কথাটা এমন করে বললে!
সুরেশ্বর বললে—ব্রজদারো চা জলখাওয়ানোর ভার তোর উপর রইল অর্চি!
—তোমাদের দুজনকেও খাওয়াব। সন্ধ্যে করে উঠে চা খেয়ে রান্না চড়াব। ঠাকুরকে বলে এসেছি-আমি আসছি। রান্না আমি করব। আরও আছে, তাও বলব।—তোমার কথা তুমি শেষ কর। কথা নয়—জবানবন্দী। কতদূর হ’ল?
সুরেশ্বর বললে-শ্যামাকান্ত সৌভাগ্যশিলা নিয়ে কালীঘাট ফিরছেন!
অৰ্চনা চলে গেলে সুলতা বললে—বড় ভাল মেয়ে।
—হ্যাঁ। রায়বাড়ীর সব শুভ, সব কল্যাণের ভাণ্ডার হল মেয়েটি।
—কিন্তু লেখাপড়া শেখাও নি কেন? এইসব মেয়ে কি হত বল তো? হেসে সুরেশ্বর বললে-অৰ্চনা এম-এ পাস করেছে সুলতা।
–এম-এ পাস করেছে?
—হ্যাঁ। বিধবা হবার পর কি করব, ওকে পড়িয়েছিলাম। টপটপ করে পাশ করে গেল। হিন্দু ফিলজফি খুব ভাল করে পড়েছে। তার জন্যে সংস্কৃত পড়েছে বাড়ীতে।
চুপ করে রইল সুলতা।
সুরেশ্বর বললে—ওর কথা এখন থাক সুলতা। ওর লেখাপড়া শেখার সময় ও যখন বি-এ পড়ে, তখন আর একজন ওর সঙ্গে পড়ত। সেসব কথা সবই শুনবে। সবই রায়বাড়ীর জবানবন্দীর অন্তর্ভুক্ত। এখন একশো তেত্রিশ বছর আগে ফিরে চল। কীর্তিহাট রঙ্গমঞ্চে রায়বাড়ী নাটকের তখন প্রথম অঙ্কের শেষ দৃশ্য প্রায়। কুড়ারাম রায়-ভটচাজ নাটক শুরু করে দিয়ে গত। সোমেশ্বর নায়ক, তাঁর সন্তান নেই। তাঁর সঙ্গে শ্যামাকান্তের দেখা হয়েছিল কালীঘাটে। সৌভাগ্যশিলা পেয়ে শ্যামাকান্ত পাগলবাবা সিদ্ধির প্রত্যাশায় প্রমত্ত হয়ে উঠেছেন। সিদ্ধি তাঁকে পেতেই হবে। সৌভাগ্যশিলা তাঁর সহায়। তাঁর কথা নাকি তখন ফলতে শুরু করেছে। যাকে বলে বাক্সিদ্ধি। তখন তাঁর ভক্ত জুটেছে। কেউ আসে রোগের জন্য, কেউ আসে বিপদের জন্যে। শুনেছি, বশীকরণের জন্যেও ধনী গৃহিণীরা আসতেন, আবার ধনীজনেও আসতেন জুড়ি হাঁকিয়ে।
তখন সতীনের যুগ। বড়লোকদের তিন-চার স্ত্রী, কি তারও বেশী স্ত্রী থাকতেন। তাঁদের গৃহিণীদের মধ্যে স্বামী সমাদরের প্রতিযোগিতা চলত। সে যত্নসেবা থেকে বশীকরণ পর্যন্ত নানান পথে চলত সতীনে সতীনে লড়াই। ধনীরা আসতেন কোন মোহিনী বাঈকে বশ করবার জন্য। সন্তানহীন সোমেশ্বর কিন্তু দ্বিতীয় বিবাহ করেন নি। বারো-তেরো বছর বয়সে পৈতে হওয়ার পরই ন্যাড়ামাথায় পিতার বান্ধবীর কন্যা রাজকুমারী কাত্যায়নীকে বিয়ে করেছিলেন। এবং তাঁর সঙ্গে বাল্যখেলার মধ্য দিয়ে যে প্রেমে তিনি পড়েছিলেন, তার অপমান তিনি করেন নি। কাত্যায়নীর মা নিঃস্ব রাজার গৃহিণী হলেও সত্যকারের রাণী-বুদ্ধির অধিকারিণী ছিলেন। তিনি মেয়ের সতীনের পথে কাঁটা দিতে বাছাই করে বাইরে সুন্দরী বাঈজী এবং ঘরে রূপসী দাসী রেখে দিয়েছিলেন, সোমেশ্বর রায়কে আর বিবাহের ভাবনা ভাবতেই দেন নি। আরও একটা কুট চাল চেলেছিলেন তিনি। বড় বড় গণৎকার ডেকে তাঁদের দিয়ে বলিয়েছিলেন, সন্তান হয়ে নষ্ট হওয়া হেতু সোমেশ্বরেরই গ্রহসংস্থানের দোষ। তিনি শত বিবাহ করলেও সন্তান বাঁচবে না, যতক্ষণ না এই গ্রহরোষের উপযুক্ত শান্তি না হয়। গণৎকারেরা রাজকুমারী কাত্যায়নীর মায়ের কাছ থেকে বিদায় পেতেন, আবার গ্রহশান্তি যজ্ঞেরও সুযোগ পেতেন।
এর মধ্যে সোমেশ্বর রায় তাঁর মামাতো ভাইয়ের কাছে সন্ধান পেয়েছিলেন কালীঘাটের এই পাগলাবাবার। তখন তিনি গ্রহযোগ করে প্রায় হতাশ হয়েছেন। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের পরামর্শে স্ত্রীকে সাহেবডাক্তার দেখাচ্ছেন। রাজকুমারী কাত্যায়নী তখন অন্তঃসত্ত্বা। মেয়ে বিমলা তখন তাঁর গর্ভে এসেছেন। তবুও মামাতো ভাইয়ের মুখে এই সাধুর কথা শুনে কালীঘাট এসে পাগলাবাবার শরণ নিলেন।
পাগলাবাবা সোমেশ্বরকে চিনতেন। পদ্মনাভ ভটচাজের গানপাগল জামাই শ্যামাকান্ত বছরে একবার কালীপুজোর বিপুল উৎসবে শ্যামনগর থেকে কীর্তিহাটে যেতেন। তখন উৎসবের মধ্যে ওস্তাদী গানের একটা আসর হত। বাঈজী নাচ আসত কলকাতা থেকে। শ্যামাকান্তের এই ছিল প্রধান আকর্ষণ। ওস্তাদী আসরে তিনি গানও গেয়েছেন, তবলা—পাখোয়াজে সঙ্গতও করেছেন। কাপড়, চাদর এবং তার সঙ্গে পাথেয় দক্ষিণা নিয়ে আসতেন।
তিনি তাঁকে দেখেই তাঁকেও চিনেছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়েছিল কীর্তিহাটের কোলে কাঁসাইয়ের ওপারে জঙ্গলের মধ্যে সিদ্ধাসনের কথা। সিদ্ধাসনের কথা মধ্যে মধ্যে মনে পড়ত তাঁর। ওখানকার সিদ্ধসাধক তারাদাস চক্রবর্তীর কথা তিনি শুনেছিলেন, জানতেন। চক্রবর্তী ওখানে পঞ্চমুণ্ডীর আসন করেছিলেন। সে আসনও আছে। কিন্তু ওখানকার কাছেও কেউ যায় না। কারণ ওই শিমুলতলায় তারাদাস চক্রবর্তীর নায়িকার আত্মা আজও ঘুরে বেড়ায়। চক্রবর্তী তাঁকে ওখানে আসন পাহারা দিতে রেখে গেছেন। বিচিত্র কাহিনী তার। চক্রবর্তী প্রথম যোগিনী-সাধন করে সিদ্ধ হন। তারপর তারই কৃপায় এবং সাহায্যে পেয়ে- ছিলেন শক্তিসাধনায় সিদ্ধি। রাজা যদুরাম রায় তাঁকে নিষ্কর দিয়েছিলেন এই জঙ্গল। পরে এ জঙ্গল মহল চিতরং কিনেছিলেন কুড়ারাম রায় ভটচাজ। সিদ্ধাসন একসময় প্রলুব্ধ করেছিল শ্যামাকান্তকে। কিন্তু তখনও তিনি গৃহী। তাঁর সাহস হয়নি।
এ সিদ্ধাসন এবং এই বন তখন নাকি যোগিনী-রক্ষিত ছিল।
সোমেশ্বর রায়ও শ্যামাকান্তকে চিনেছিলেন এবং বিস্মিতও হয়েছিলেন। এ তো সেই শ্যামনগরের ভট্টচাজবাড়ীর পদ্মনাভ ভটচাজের জামাই। কিন্তু তবুও শ্যামাকান্তের কথাবার্তা শুনে বুঝেছিলেন, এ মানুষ সে মানুষ নয়। মানুষটা আলাদা হয়ে গেছে। চোখের চাউনিতে কথায়বার্তায়, হাসিতে তিনি বিশ্বাস করেছিলেন, এ সিদ্ধ হয়েছে।
শ্যামাকান্তও ভরসা দিয়ে বলেছিলেন—হবে। হবে। বাঁচবে ছেলে। হে-হে-হে। কিন্তু যজ্ঞ করতে হবে। করব আমি, আর ওষুধ দোব। খেতে হবে। হ্যাঁ।
সোমেশ্বর বলেছিলেন—তাই করুন।
শ্যামাকান্ত বলেছিলেন—হে-হে, সে এখানে নয়। বুঝেছ! কীর্তিহাটে যেতে হবে। ওখানে সিদ্ধেশ্বরীর আসন আছে, সেখানে, সেখানে করব যাগ
—সেখানে!
—হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমি যাগ করব, ভার আমার, তোমার ভয় কি?
সোমেশ্বর রায় তাই করেছিলেন। শ্যামাকান্তকে নিয়ে সস্ত্রীক এসেছিলেন কীর্তিহাটে। সুরেশ্বর বললে—এসব কথা কাল তোমাকে বলেছি সুলতা। বলিনি শুধু শ্যামাকান্ত এবং সোমেশ্বরের গোপন কথা। সে কথা লোকেরা কেউ জানত না। পরে একথা জেনেছিল দুজন। একজন গৌহাটিতে মহেশচন্দ্র। অন্যজন রামব্রহ্ম ভটচাজ, সোমেশ্বরের কুলপুরোহিত। মৃত্যুর পুর্বে সোমেশ্বর তাঁকে ডেকে সব কথা বলে গিয়েছিলেন। দুজনের দুখানা চিঠিই এই রয়েছে। দুজনেই লিখেছিলেন বীরেশ্বর রায়কে। দুজনের চিঠিতেই এক কথা। ঘটনায় এতটুকু অমিল নেই। তফাৎ শ্যামাকান্ত মহেশচন্দ্রকে যা বলেছিলেন, তাতে শ্যামাকান্তের দোষ নেই। আর সোমেশ্বর রায় রামব্রহ্ম ভটচাজকে যা বলেছিলেন—তাতে তাঁর নিজের দোষ থাকলেও তা শ্যামাকান্তের থেকে কম!
মহেশচন্দ্রের চিঠিতে রয়েছে, শ্যামাকান্ত তাঁকে বলেছিলেন-জানিস, সোমেশ্বর রায়ের সন্তান বাঁচাবার জন্যে কীর্তিহাটে যজ্ঞ করলাম। প্রথম যাগ করেছিলাম রায়দের কালীমন্দিরের সামনে। সামনে রাখলাম আমার সৌভাগ্যশিলাকে। কিন্তু মনে হল, হল না ঠিক। পূর্ণাহুতি দিলাম, শিখাটা জ্বলে উঠে দপ্ করে নিভে গেল! কেউ যেন ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিলে। মনটা খারাপ হল। ভাবলাম, এ কি হল? তারপর কারণটা পেলাম। সেই দিনই গেলাম ওপারে সিদ্ধাসনের জঙ্গলে। সোমেশ্বর বললে—আপনি যাবেন ওখানে, কিন্তু ওখানে। মানে লোকে বলে, যোগিনী আছে।
লোকে গেলে ভয় পায়।
শ্যামাকান্ত বলেছিলেন—ভয়! ধুর! বলে হেসেছিলেন। তারপর বলেছিলেন—যোগিনীর ব্যাপারটা কিছু জান? শুনেছ?
সোমেশ্বর নাকি বলেছিলেন-লোকে বলে যে, চক্রবর্তী প্রথম যোগিনীসিদ্ধ হয়েছিলেন। সেই যোগিনী ছিলেন তাঁর নায়িকা। তাঁর সাহায্যেই তিনি কালীসিদ্ধ হন। চক্রবর্তী সেই নায়িকাকে এখানকার আসন আর এই বন পাহারা দিতে রেখে তীর্থ করতে গিয়েছিলেন। বলে গিয়েছিলেন তিনি ফিরে না আসা পর্যন্ত সে যেন এই স্থান ছেড়ে না যায়। নাহলে জন্তু-জানোয়ারে, চোর-ডাকাতে, ভ্ৰষ্টমানুষে এসে এ আসন অশুদ্ধ করে দেবে। যোগিনীকে প্রতিজ্ঞা করিয়েছিলেন। আর বাড়িতে বলে গিয়েছিলেন ভাইপোদের, যেন ওই বনের ধারে পাতায় যোগিনীকে ভোগ দিয়ে আসে। আজও সে ভোগ আমার এস্টেট থেকে যায়। কারণ ওই জঙ্গল আমরা কিনেছি, আমার এলাকা। তা চক্রবর্তী সেই তীর্থে গিয়ে আর ফেরেন নি। কোথায় মারা গিয়েছেন, কেউ জানে না। কেউ কেউ বলে—হিমালয়ে তপস্যা করছেন, ওঁরা তো যতদিন ইচ্ছে বাঁচতে পারেন। কোনদিন আসবেন। তিনি এলে যোগিনীর মুক্তি হবে। এখন ওই একবেলা ব্রাহ্মণে পাতায় করে একটা ভোগ নামিয়ে দিয়ে আসে। তাছাড়া ওর ত্রিসীমানায় কেউ যায় না। গেলে মুখে রক্ত উঠে মরে যায়।
শ্যামাকান্ত বলেছিলেন—ওই বনেই আমাকে আসন করতে হবে। ওখানে একটা যাগ করব। বুঝেছ রায়বাবু, ওই যোগিনীর দৃষ্টিতেই তোমার সন্তান বাঁচে না। এবার আমি বুঝেছি। তোমাকে আমার উত্তরসাধক হতে হবে। সাহস আছে? দীক্ষা নিয়েছিস?
—হ্যাঁ।
—তবে ঠিক আছে। তোকে পুরশ্চরণ করিয়ে শুদ্ধ করে নোব। আমি জপ করব, তুমি পাহারা দেবে, বুঝলে!
তাই করেছিলেন শ্যামাকান্ত। দিনের ভাগে সেই দিনই তিনি বনের ভিতর ঢুকেছিলেন। শিমুলতলার আসন দেখে ফিরে এসে বলেছিলেন, ঠিক আছে।
তারপর তিথি দেখে তিনি বনে গিয়ে আসনের আশপাশের জঙ্গল নিজে হাতে পরিষ্কার করে ফিরে সোমেশ্বরকে বলেছিলেন- আজ যাব। তৈরী থাকবে। ভয় করবে না। বুঝলে। এর নাম বীরাচার। বীর ছাড়া এ আচার অন্যের নয়।
মহেশচন্দ্র লিখেছিলেন—দুইটি শ্লোক তিনি বলিয়াছিলেন, সে শ্লোক অদ্যাপি আমার মনে রহিয়াছে। “মহাবনো মহাবুদ্ধিধর্মহাসাসিক শুচিঃ। মহাস্বচ্ছো দয়াবাংশ্চ সর্বভুতহিতেরতঃ।” এই হইল বীরাচারীর লক্ষণ। আর উত্তরসাধক যিনি হইবেন, তাঁহাকেও হইতে হইবে সমান গুণসম্পন্ন। “সমান গুণসম্পন্নঃ সাধয়ে-দ্বীভভী স্বয়ম্।” এবং উত্তরসাধককে শাস্ত্র-পাণি হইতে হইবে। আমি সঠিক বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারি নাই, তবে এইটি বুঝিয়াছিলাম যে, যাহারা দুঃসাহসী এবং কৌশলী তাহারা সবই পারে!
শ্যামাকান্তকে জিজ্ঞাসাও করিয়াছিলাম, তুমি যোগিনীকে দেখিয়েছিলে?
শ্যামাকান্ত আমাকে বলিয়াছিলেন-ওরে মূর্খ, তোর এখনও বিশ্বাস হইল না? ওরে, রাত্রে আমি আসনে জপে বসিলাম, সে খসখস শব্দ করিয়া আশেপাশে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। ফোঁসফোঁস করিয়া নিঃশ্বাস ফেলিল। ওরে, আমার সম্মুখে ধুনি ছিল, সম্মুখে আসিতে পারিল না, পৃষ্ঠদেশের অতীব নিকটে দাঁড়াইয়া নিঃশ্বাস ফেলিল, কিন্তু আমাকে স্পর্শ করিতে পারিল না। কারণ রক্ষামন্ত্রে আমার অঙ্গবন্ধন করা ছিল। আমি স্বহস্তে ভোগ রন্ধন করিয়া ভোগ দিয়া কিছুটা দুরে রাখিয়া দিলাম এবং অপেক্ষা করিয়া রহিলাম, সে শিবামুর্তিতে আসিয়া ভোগ গ্রহণ করিয়া চলিয়া গেল। তবুও বলিবি—যোগিনী দেখিয়াছ? তুই এসব বুঝিবি না। দীক্ষা না হইলে ইহা বুঝিতে পারা যায় না রে মূর্খ!
আমি বলিয়াছিলাম, বুঝাইয়া বলিলে বুঝিব না কেন?
শ্যামাকান্ত বিচিত্র উত্তর দিয়াছিলেন—ওরে বেটা, জলে চিনি ফেললেই গলিয়া যায়, তাহা তুই দেখিয়াছিস বলিয়াই বুঝিতে পারিস। যে দেখে নাই তাহাকে কিরূপে বুঝাইবি? ওরে মূর্খ, প্রস্তরের মধ্যে হীরক থাকে, তাহা যে হীরক চেনে সেই ব্যক্তিই চিনিতে পারে। অপরকে তাহা হীরক বলিয়া বিশ্বাসই করিতে হয়।
উত্তর শুনিয়া আমি অবাক হইয়া গিয়াছিলাম।
এরপর শ্যামাকান্ত যা বলেছিলেন, তা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন মহেশচন্দ্র। কিছুদিনের মধ্যেই নাকি দেহধারিণী হয়ে যোগিনী এসেছিলেন তাঁর সম্মুখে।
সে এক শ্যামাঙ্গী যুবতী, পাগলিনী। কীর্তিহাটের কেউ তাকে চিনত না, দেখে নি। হঠাৎ সে একদিন এল কোথা থেকে, রূপ ছিল পাগলিনীর। কিন্তু অতি উগ্র সে, অর্ধউলঙ্গ মেয়েটা দাঁত কড়মড় করতে করতে বিড়বিড় করে বকত। মানুষজনকে অভিসম্পাত আর গালিগালাজ দেওয়াই ছিল তার কাজ। হাঁ-হাঁ করে বাড়িতে ঢুকে যা সামনে পেত তাই কেড়ে খেয়ে নিত। গৃহস্থেরা তাড়া করলে সে যা হাতের কাছে পেত, তাই নিয়ে আক্রমণ করত গৃহস্থকে। হাতে একটা লাঠি কিংবা গাছের ডাল, কিছু না পেলে ঢেলা, তাই ছিল অস্ত্র। এ ছাড়াও নখ আর দাঁত, আদিম অস্ত্র মানুষের। কিন্তু গ্রামের লোকে দলবদ্ধ হয়ে তাকে তাড়া করেছিল, সে ছুটে এসে ঢুকেছিল রায়দের ঠাকুরবাড়ীতে। শ্যামাকান্ত তখন মাকালীকে ভোগ দিয়ে যোগিনীর ভোগ নিয়ে চলেছেন সিদ্ধাসনের জঙ্গলে ভোগ দিতে। মেয়েটা ছুটে এসে সন্ন্যাসী শ্যামাকান্তকে বলেছিল, আমাকে মারছে, আমাকে বাঁচাও, ও সন্ন্যেসীঠাকুর, আমাকে বাঁচাও। তখন সে মার যথেষ্ট খেয়েছে। কপাল কেটে গেছে। হাতে বুকে প্রহারের দাগ। শ্যামাকান্ত তার মুখের দিকে তাকিয়ে লোকজনদের বলেছিলেন—চলে যাও। ওকে মেরো না। এ মানুষ নয়। একে ভর করেছে কোন ডাকিনী যোগিনী।
পাগলিনী এবার হাত বাড়িয়ে কেড়ে নিতে গিয়েছিল শ্যামাকান্তের হাতের যোগিনীর ভোগ।
শ্যামাকান্ত তৎক্ষণাৎ চিনেছিলেন তাকে ওই যোগিনী বলে। তিনি তাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন ওই ওপারের জঙ্গলে এবং তাকে পরিতৃপ্ত করে যোগিনীর ভোগ খাইয়ে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন—চলে যাবি? না থাকবি?
—সে বলেছিল—খেতে দেবে?
—রোজ তো শেয়াল হয়ে খেয়ে যাস। আজ পাগলী সেজে এসেছিস। চালাকি করছিস?
মেয়েটা খিল-খিল করে হেসেছিল।
শ্যামাকান্ত বলেছিলেন—শান্ত হয়ে থাকিস তো থাক। রোজ খাবি। কাপড় দোব, খেতে দোব। তেল দেব, মাথায় মাখবি। অনেক জিনিস দেবো। শুধু শান্ত হয়ে থাকতে হবে। কাউকে মারতে পাবি নে। কাউকে শাপ-শাপান্ত করবি নে। আমি যা বলব শুনবি। নে, এবার পান খা!
যোগিনীর ভোগের জন্য পান ছিল, সেই পানও তাকে খাইয়েছিলেন। এবং বলেছিলেন- আর অনিষ্ট করবিনে তো?
—না। না।
—বেশ। ওইখানে শুয়ে ঘুমো। আমি ওবেলা আসব।
শ্যামাকান্ত বলেছিলেন, ওই যোগিনী কোন পাগলিনী নারীদেহকে আশ্রয় করে তাঁর মন্ত্র আকর্ষণে আসতে বাধ্য হয়েছে।
সেই দিনই শ্যামাকান্ত তন্ত্রসার শাস্ত্রের বীরাচারমতে কনকাবতী যোগিনী-পূজাসম্মত পূজা করেছিলেন তার। তাকে স্নান করিয়ে, মাথায় তেল দিয়ে, চুল আঁচড়ে, কপালে সিঁদুরের টিপ পরিয়ে, পায়ে আলতা দিয়ে, নূতন লালপেড়ে শাড়ী পরিয়ে তার অর্চনা করেছিলেন।
সোমেশ্বরও সেদিন হাতে একখানা তলোয়ার নিয়ে সিদ্ধাসন থেকে খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে উত্তরসাধকের কাজ করেছিলেন, পাহারা দিয়েছিলেন।
এর পর থেকে শ্যামাকান্ত ওই সিদ্ধাসনের জঙ্গলেই আস্তানা গেড়েছিলেন। কাজ হয়েছিল ওই যোগিনী পাগলীর সেবা, তাকে পূজার্চনা করে তুষ্ট করা। শুধু একবার আসতেন সকালে। এসে স্নান করে সৌভাগ্যশিলার অর্চনা সেরে মায়ের প্রসাদী ভোগ নিয়ে চলে যেতেন ওই সিদ্ধাসনের জঙ্গলে। মাসখানেক পর যোগিনীকে নিয়ে এলেন শ্যামাকান্ত। পোষা জন্তুর মত সে শ্যামাকান্তের পিছন পিছন গ্রামে এসে ঢুকল।
সেদিন সমস্ত কীর্তিহাটের লোকেরা তাকে দেখে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। লালপাড় শাড়ী পরনে একটি শ্যামাঙ্গী লাবণ্যময়ী মেয়ে। দাঁত কড়মড় করছে না। কাউকে মারতে যাচ্ছে না। নিজের বেশভূষা নিয়েই সে প্রমত্ত। কাপড় ঝাড়ছে। হাতের শাঁখা দেখছে। আর ফিকফিক করে হাসছে। মন্দিরের নাটমন্দিরে এনে তাকে বসিয়ে শ্যামাকান্ত সোমেশ্বরকে বলেছিলেন—ডাক, তোমার গৃহিণীকে ডাক। যোগিনী আশীর্বাদ করবে। তাকিয়ে দেখছ কি?
সোমেশ্বরও তাকিয়ে দেখছিলেন মেয়েটাকেই। এক মাসের মধ্যে সেই অর্ধউলঙ্গ উন্মাদ পাগল ভিক্ষুক-মেয়েটার পরিবর্তন দেখে বিস্ময়ের সীমা ছিল না তাঁর। মেয়েটা পাগলের মত হাসে বটে, মধ্যে মধ্যে রেগেও উঠতে চাচ্ছে, কিন্তু তবু তার সঙ্গে এর অনেক তফাৎ। সবচেয়ে তফাৎ মেয়েটার চেহারায়।
মেয়েটার দেহে কোথাও কোন মালিন্য নেই। কাদা নেই, ধুলো নেই। চুলে জটা নেই। মুখখানায় সেই একটা উগ্র ভয়ঙ্কর ভাব নেই। শ্যামবর্ণা মেয়েটা কোমলাঙ্গী হয়ে উঠেছে, একটি লাবণ্য যেন ফুটে উঠতে শুরু করেছে।
রাজকুমারী কাত্যায়নী গরদের শাড়ী পরে এসে তার সামনে আসনে বসেছিলেন।
শ্যামাকান্ত যোগিনীকে বলেছিলেন—নে, আশীর্বাদ কর। বল, ছেলে হয়ে বাঁচুক তোমার। বল। খুব ভাল ভাল মিষ্টি খেতে দেবে রাণীমা। বল!
যোগিনী খুব খুশী হয়ে বলেছিল—বাঁচবে, বাঁচবে, বাঁচবে।
এই সব ব্যাপারে কেউ কোন কথা বলে নি, বলতে সাহস করে নি। একমাত্র পুরোহিত রামব্রহ্ম ন্যায়রত্ন বলেছিলেন- দেখুন রায়মশায়, আমি আপনার পুরোহিত বলেই বলাটা কর্তব্য মনে করি, যদি অনুমতি দেন তো বলি।
—বলুন।
—আমি কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের জ্ঞাতিবংশীয়। তন্ত্র আমি জানি। জানি বলেই আমাকে আপনার পিতা এখানে এনে বসবাস করিয়ে মায়ের পূজোর ভার দিয়েছেন। আপনি যজমান। গৃহী। রাজাতুল্য ব্যক্তি। কুলাচারে আপনারা দক্ষিণাচারী। শুদ্ধমতে আমরা মা বলে তাঁকে আহ্বান করি, পূজা করি। সেই মতে মায়ের প্রতিষ্ঠাও হয়েছে। এখন বামাচার বা বীরাচার করতে গেলে অনিষ্ট হবে রায়বাবু। লোকটা বামাচারী। তার উপর—।
সোমেশ্বর এ সব বুঝতেন না তা নয়। বুঝতেন। রামব্রহ্ম ন্যায়রত্ন আগমবাগীশের দুরের জ্ঞাতি, তিনি আগমবাগীশের ভিটেতে যাঁরা আছেন তাঁদের কাছে মন্ত্রদীক্ষা নিয়েছেন। তন্ত্রমতে নিত্য আহ্নিকসন্ধ্যা করেন। বোঝেন সব। তিনি ভাবছিলেন। ন্যায়রত্নকে থামতে দেখে বললেন-আর কি বলুন দেখি?
—মানে লোকটি মায়ের ঘরে বসে বামাচারে পুজো করে, কারণ করে, সেই হাতেই বেলপাতা নিয়ে মাকে দেয়, সে তো হল। না হয় বুঝলাম যিনি দক্ষিণাকালী তিনিই বামাকালী, যেমন ভাবে যে তাঁকে চাইবে তেমনি ভাবেই তাঁর সাক্ষাৎ বলুন প্রসাদ বলুন পাবে। কিন্তু ওই যে নারায়ণশিলাটি, যেটি ও সঙ্গে করে এনেছে, সেটির পুজোও সে ওই কারণের হাতেই করে। ও শিলাটি বড় দুর্লভ শিলা। রাজার ঘরে উনি রাজরাজেশ্বর, সন্ন্যাসীর কাছে, সাধুর কাছে উনি সাক্ষাৎ চৈতন্যময় ব্রহ্মানন্দ। অনাচার করছে ও, অপরাধ ওর বটে কিন্তু আপনার গৃহে তো হচ্ছে সেই অনাচার। দেখুন, স্থান, মৃত্তিকা এতেও তো পাপপুণ্য অর্শায়। ওই অপরাধ আপনার গৃহকে অর্শাচ্ছে তো! গৃহের কল্যাণ-অকল্যাণ আছে। দোষযুক্ত জমি, দোষযুক্ত ভিটে এ তো লোকে কেনে না, দান করলেও নেয় না। সুতরাং—। তা ছাড়া ওই পাগলীটাকে ও যোগিনী বলছে, তারও তো কোন নিশ্চয়তা নেই!
সোমেশ্বর একটু ভেবে বলেছিলেন-দেখুন, মাস দুয়েকের মধ্যেই সন্তান হবে রাজকুমারী রাণীবউয়ের। এ একটা মাস আমার সহ্য না করে উপায় নাই। যজ্ঞটজ্ঞ করলে। ফলটা দেখতে হবে তো!
ন্যায়রত্ন বলেছিলেন—অন্ততঃ আপনি বলুন, ওই শিলাটির পূজা আমি করি। আর স্বতন্ত্র স্থানে করি। শক্তি আর বিষ্ণু দুয়ের পূজার মত আলাদা। ভজনসাধনের পথ আলাদা। কেউ বলে মা আর ছেলে। কেউ বলে যিনি শ্যাম, তিনিই শ্যামা। তবু সব বিপরীত। বিশ্বপত্রে মায়ের পুজো তুলসীপত্রে প্রভুর পুজো। এঁর রক্তচন্দন ওঁর শ্বেত অগুরু চন্দন। এঁর জবা, ওঁর শ্বেতকরবী, মালতী। বলুন, আপনার ঝঞ্ঝাট, রোজ সকালে ছুটে আসেন। মানে সন্তুষ্ট করে, কোনরকমে বুঝিয়ে আর কি!
—বলব। এই তিনদিন পর শনিবার চতুর্দশীতে উনি শেষ যাগ করবেন, ওই সিদ্ধপীঠে সেটা হয়ে যাক, তারপর বলব।
—বেশ। এতদিন, আজ তিনমাস চলছে, আর তিনদিন চলুক!
তিনদিনের সকালে সোমেশ্বরকে কথাটা বলতে হয় নি। সন্ন্যাসী শ্যামাকান্তই এসে বলেছিলেন, রায়বাবু! আজ তোমার ন্যায়রত্ন ঠাকুরকে বলো, নারায়ণের পুজোটা করতে। বুঝেছ? আর সব উয্যুগ যেন ঠিক সময়ে গিয়ে পৌঁছয়। আমার উপোস। কিন্তু মনোহরা তো উপোস করবে না। তার ভোগ পাঠিয়ে দিয়ো।
সোমেশ্বর বুঝেছিলেন সেই মেয়েটির কথা বলছেন শ্যামাকান্ত। তবু বিস্ময় প্রকাশ করেই বলেছিলেন—মনোহরা?
হে-হে করে হেসে শ্যামাকান্ত বলেছিলেন, পাগলী সেজে চোখে ধুলো দেবে ভেবেছিল যোগিনী! বুঝেছ, পাগলী সেজে ধুলোকাদা মেখে রূপ ঢাকা দিয়েছিল। আমি দেখেই চিনে- ছিলাম। যোগিনী মনোহরা যোগিনী—শ্যামবর্ণা আয়তনয়ন, কোমলাঙ্গী পরিপূর্ণা যুবতী, সেদিন দেখেছ, আজ দেখবে! আজ তোমার উপবাস, তোমার গৃহিণীর উপবাস, রাত্রে তুমি সারারাত্রি উপস্থিত থাকবে। পূর্ণাহুতির পর তিলক নেবে। মনোহরার আশীর্বাদ নেবে। দেখবে তাকে।
সোমেশ্বর ন্যায়রত্নকে ডেকে খুশী হয়ে বলেছিলেন—হয়ে গেছে ন্যায়রত্নমশাই। নিজেই এসে বলে গেলেন, ওহে, আজ ন্যায়রত্নকে বলো, নারায়ণের পুজো করতে। বুঝেছ!
—ওইটে ওঁর কাছে কায়েম করে নেবেন।
—নেব, বলব। যাগটা হয়ে যাক। আচ্ছা, আর একটা কথা। কনকাবতী নামে যোগিনী আছে?
—হ্যাঁ আছে, সুরসুন্দরী, কনকাবতী, মনোহরা, কামেশ্বরী, রতিসুন্দরী, মধুমতী, পদ্মিনী যোগিনী অনেক, চৌষট্টি যোগিনী, তার মধ্যে মানুষে ওই আট-দশটি যোগিনীসাধনই করে।
—মনোহরা যোগিনী কি শ্যামবর্ণা?
—হ্যাঁ, কুরঙ্গনেত্রাং শরদিন্দুবক্রাং বিম্বাধরাং চন্দনগন্ধলিপ্তাং চীনাংশুকাং পীনকুচাং শ্যামাং কামদুঘাং বিচিত্রাং। ওই হল ওঁর ধ্যান!
সেদিন রাত্রের অভিজ্ঞতায় সোমেশ্বর রায় অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন। সে রাতের অভিজ্ঞতার কথা তিনি বলেছিলেন রামব্রহ্ম ন্যায়রত্নকে। বলেছিলেন—সে আমি বর্ণনা করতে পারব না ন্যায়রত্নমশাই! সে কি যাগ! কি পূর্ণাহুতি! আমি তো সারাক্ষণ দুরেই দাঁড়িয়ে ছিলাম। আমার কাছ থেকে আরও স’রে কাঁসাইয়ের গর্ভে বসেছিল, শিবে আর তারা। আর হরি চাঁড়াল। বুঝলেন, থমথম করছে রাত্রি, চতুর্দশীর অন্ধকার। বনের মধ্যে ঝিঁঝি ডাকছে, প্রহরে প্রহরে শিবারব। তারই মধ্যে শ্যামাকান্ত হাঁকছেন, কালী কালী কালী। আর ডাকছেন, মনোহরা, মনোহরা। খলখল করে যোগিনী হাসছে। পূর্ণাহুতির সময় গেলাম, ডাক পড়ল। তখন দেখি তাঁর চোখদুটো রক্তবর্ণ, হোমের ধুনি গনগন করছে। আর যোগিনী সামনে থমথমে হয়ে বসে আছে, পরনে লাল চেলী, গলায় ফুলের মালা, হাতে শঙ্খ, তার সঙ্গে চুড়ি, রুক্ষ এলোচুল, কপালে সিঁদুরের ফোঁটা, এই বড় চোখ দুটো লাল হয়ে ঢলঢল করছে। শ্যামবর্ণ রঙ-ধুনির আলোয় সে যে কি লাগছিল কি বলব! চোখদুটি ঠিক হরিণের চোখ। তার উপর কারণের ঘোরে রাঙা লাগছে। যেন ভর লেগেছে। তারপর আমাকে কারণ দেবার জন্যে পাত্রতে কারণ ঢেলে যোগিনীকে দিয়ে বললেন—মনোহরা, দে, রায়বাবুকে প্রসাদ করে দে। নিয়ে কি করলে জানেন? বললে—তু খা, খেয়ে ওকে দে। তারপরে আমাকে দিবি। এই বাবু, আমার এঁটো খাবি?—খাস না। ওই ওর এঁটো খা। আমার মনের কথা কি করে বুঝলে বলুন?
চুপ করে ছিলেন রামব্রহ্ম। তারপর জিজ্ঞাসা করেছিলেন—পূর্ণাহুতি কেমন হল বলুন।
—ভাল। ভাল। একবারে দু’হাত উঁচু হয়ে জ্বলল। তারপর আ-স্তে আ-স্তে নিবে এল।
এরপর থেকে শ্যামাকান্ত ওইখানেই আস্তানা গেড়েছিলেন। প্রথম খড়ে-বাঁশে চালা আর রায়বাড়ীর পাঁজা থেকে ইট নিয়ে গিয়ে ইট পেড়ে মেঝে করে নিয়েছিলেন। তারপর বাঁশের বেড়া দিয়ে তার গায়ে মাটি ধরিয়ে দেওয়াল। দুখানা কামরা। একখানায় শ্যামাকান্ত, একখানায় যোগিনী।
ঠিক পনের দিন পর কলকাতা থেকে একটা আশ্চর্য সুখবর এসেছিল। সোমেশ্বর রায় একটা হারপাল্লার মামলায় আশ্চর্যভাবে জিতেছেন। জিতেছেন খোদ কোম্পানীর বিরুদ্ধে। নুনের খালারির মামলা। কোম্পানী খালারি খাস করেছিল। তিনি ক্ষতিপূরণ চেয়েছিলেন। খালারির জমি কোম্পানী নিয়েছিল কিন্তু খাজনা-কমি দেয়নি। সে খাজনা-কমির মামলায় ডিগ্রী পেয়েছেন। দশ হাজার টাকার ডিগ্রী!
প্রিন্স দ্বারকানাথ নুনের দেওয়ান ছিলেন। তিনি পর্যন্ত বলেছিলেন- মামলা করে দেখ একটা কিন্তু কিছু হবে বলে মনে হয় না। তবু দেখ।
উৎসব পড়ে গিয়েছিল কীর্তিহাটের কাছারীতে। রামব্রহ্ম ন্যায়রত্ন বলেছিলেন—এ আপনার গৃহে সৌভাগ্যশিলার আশীর্বাদ বাবু!
শ্যামাকান্তের কাছে গিয়েছিলেন, শ্যামাকান্ত হা-হা করে হেসে বলেছিলেন—এখন হয়েছে কি রায়বাবু, তোমাকে আমি রাজা করে দোব।
যোগিনীকে ডেকেছিলেন, মনোহরা!
মনোহরা যোগিনী তখন মানুষের মত। তবে ছোট মেয়ের মত আবদেরে। সে এসে সরাসরি শ্যামাকান্তের কোলে এসে বসেছিল। ডাকছিস ক্যানে?
—রায়বাবুর মামলা জিৎ হয়েছে। কি চাই তোর বল!
—লাল টকটকে কাপড়। আর সন্দেশ। খুব ভাল মণ্ডা।
—বাবুকে রাজা করে দিতে হবে।
—হবি রাজা হবি!
—ছেলে বাঁচাতে হবে।
—হ্যাঁ, রাঙা ছেলে হবে।
—কি ছেলে হবে? বেটী, না, বেটা?
—বিটী হবে, বেটা হবে, সব হবে।
এর সপ্তাহখানেক পরেই হয়েছিল রাজকুমারী কাত্যায়নীর এক কন্যাসন্তান। এবং আশ্চর্য, কন্যাটি পূর্বের সন্তানদের মতো মৃতসন্তান হয়নি। জীবিত কন্যা—সরবে কান্না কেঁদে তার আসার সংবাদ ভূমিষ্ঠ হতে হতেই ঘোষণা করে জানিয়েছিল।
সোমেশ্বর রায় মামলায় জেতা দশ হাজার টাকা দিয়ে শুরু করলেন সৌভাগ্যশিলার মন্দির। আর ওই সিদ্ধাসন বাঁধিয়ে পাকা করে দিলেন। কিন্তু শ্যামাকান্ত যেন উগ্র হয়ে উঠলেন। সবকিছুতে অধীর উগ্র। উদ্ভ্রান্ত। শুধু তাই নয়, নির্যাতন শুরু করলেন ওই যোগিনী পাগলীর উপর। তাকে গালাগাল করতেন, তারপর শুরু করলেন প্রহার।
মহেশচন্দ্র তাঁর চিঠিতে লিখেছেন—শ্যামাকান্তের কথা। শ্যামাকান্ত তাঁকে বলেছিলেন—যোগিনী সোমেশ্বর রায়ের অভীষ্ট পূরণ করিল। কিন্তু আমাকে ছলনায় ভুলাইয়া প্রতারণা করিতে লাগিল।
আমি সাধনা করি, সে পূজা গ্রহণ করে কিন্তু সিদ্ধিতে সাহায্য করে না। মধ্যে মধ্যে পুজার আসনে বসিয়া আমি ধ্যান শুরু করিলেই উঠিয়া পলাইয়া যাইতে শুরু করিল। কখনও সমাদর করিয়া আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া আসন হইতে টানিয়া উঠাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল।
আমি তাহাকে বলিতাম- তোকে মারিয়া ফেলিব। সে ক্রন্দন করিত। তাহাকে গালাগালি করিতাম, সেও গালাগালি করিত। অবশেষে তাহাকে প্রহার করিয়া কহিলাম—কবে আমাকে সিদ্ধি দিবি বল?
সে বলিল—আমি জানি না।
আবার তাহাকে প্রহার করিলাম। বলিলাম—বল! বল!
সে বলিল-সিদ্ধির গাছ এখানে নাই। কোথায় পাইব?
তাহাকে প্রহার করিয়া এবার ঘরে বন্ধ করিলাম। আমি ক্রোধে ক্ষোভে উগ্র হইয়া উঠিলাম।
কয়েকদিন পর, তখন জ্যৈষ্ঠ মাস-মনোহরা একদিন পলাইয়া গেল। গিয়া উঠিল সোমেশ্বর রায়ের বাড়ীতে। তাহাকে গিয়া কাঁদিয়া সামান্য নারীর মত ছলনা করিয়া কহিল—বাবু, আমাকে বাঁচাও! আমি তখন নিদ্রিত ছিলাম। নিদ্রাভঙ্গে উঠিয়া মনোহরাকে না দেখিয়া সমস্ত জঙ্গল খুঁজিলাম। তাহার পর গেলাম রায়বাড়ী। সেখানে দেখিলাম, সে সোমেশ্বর রায়ের কন্যাকে কোলে করিয়া আদর করিতেছে।
সেখান হইতে আমি তাহাকে ধরিয়া আনিলাম। সোমেশ্বর কহিল —আপনি এমন করিয়া ইহাকে প্রহার করিতেছেন, ইহাতে আপনার কিরূপে সিদ্ধি হইবে? প্রসন্ন না হইলে কে কবে কাহাকে অভীষ্ট সিদ্ধিতে সাহায্য করিয়া থাকে!
আমি তাহাকেও গালাগাল দিয়াছিলাম।
সুরেশ্বর বললে—এর কিছুদিন পরই নেমেছিল বর্ষা। কাঁসাই ভরতে শুরু করেছিল। একদিন প্রবল বর্ষা নেমে বন্যা এসেছিল। বন্যার জল কীর্তিহাটের উঁচু বন্যারোধী বাঁধের গায়ে বাধা পেয়ে সিদ্ধপীঠের জঙ্গলে ঢুকে ডুবিয়ে দিয়েছিল সিদ্ধপীঠ!
শ্যামাকান্তের ছোট ঘরের মেঝেতে জল ঢুকেছিল। পঞ্চমুণ্ডীর আসন এবং সামনের চত্বরের উপরেও দাঁড়িয়েছিল প্রায় আধ হাত জল। অবশিষ্ট ছিল শিমুলতলার বাঁধানো গোল বেদীটা। সেটা জমি থেকে হাত তিনেক উঁচু। তারই উপর যোগিনীকে নিয়ে শুকনো কাঠে হোমকুণ্ডের আগুন দিয়ে ধুনি জ্বালিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন শ্যামাকান্ত।
মহেশচন্দ্র লিখেছেন—শ্যামাকান্ত অদ্ভুত মানুষ তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রায় চার বৎসর ধরিয়া তাঁহার সঙ্গ করিয়া তাঁহাকে যতটা বুঝিয়াছি, তাহাতে তিনি সত্যবাদী তাহাতে আমি নিঃসন্দেহ। দুরন্ত, দুঃসাহসী, ভয়লেশশূন্য। কিন্তু তাঁহার তত্ত্ব বুঝিয়াও বুঝিতে পারি নাই। ইহা জ্ঞানের দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করা হয়তো যায় না। তিনি বলিয়াছিলেন—সেই দুর্যোগ এবং অন্ধকার দেখিয়া তিনি উল্লসিত হইয়া জপে বসিয়াছিলেন। রিমিঝিমি বর্ষণ হইতেছিল, বিদ্যুৎ চমকিতেছিল; মেঘগর্জন হইতেছিল; তাঁহার মনে হইতেছিল এই দুর্যোগ-ভয়াল রাত্রে মহাশক্তির তপস্যার উপযুক্ত কাল।
মনোহরাকে পাশে বসাইয়া তিনি জপ শুরু করিয়াছিলেন। সেই দুর্যোগের মধ্যে সেদিন মনোহরা পলাইয়া যায় নাই। তাঁহার গায়ে গা দিয়া বসিয়াছিল। শিমুলগাছটা খুব ঘন নিবিড় হইলেও পাতা হইতে ঝরিয়া টপটপ করিয়া জল পড়িতেছিল। তথাপি ইহারই মধ্যে শ্যামাকান্ত জপে একেবারে মগ্ন হইয়া গিয়াছিলেন। যেন তাঁহার চেতনা ছিল না।
হঠাৎ একসময় মনোহরা তাঁহাকে ডাকিয়াছিল।—এই, এই ঠাকুর। ও ঠাকুর, শুনিতেছিস? কত জপ করিবি। ও ঠাকুর!
ধ্যান ভাঙিয়া শ্যামাকান্ত অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন—কি? কি বলিতেছিস?
সেই পাগলিনী অথবা যোগিনী বলিয়াছিল—আমার যে ক্ষুধা পাইয়াছে। আমাকে খাইতে দে। ও ঠাকুর!
শ্যামাকান্ত অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সম্মুখের ধুনিটা হইতে খানিকটা জলসিক্ত ছাই মুঠা করিয়া তুলিয়া তাহাকে দিয়া বলিয়াছিলেন—নে খা! খা!
মনোহরা ভয় পাইয়াছিল। শ্যামাকান্ত আরও ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন—খা, খা, তোকে খেতে হবে। খা! খা!
—বলিয়া তাঁহার ত্রিশুলটা লইয়া প্রহারের ভয় দেখাইয়াছিলেন।
ভয়ে মনোহরা ছাই মুখে দিয়া পরম হর্ষভরে বলিয়াছিল—ও ঠাকুর, এ যে গুড়! বলিয়া সে গব গব করিয়া সেই সিক্ত ছাইপিণ্ডটা খাইয়া ফেলিয়াছিল।
শ্যামাকান্ত সবিস্ময়ে নিজের হাতে লাগিয়া থাকা ছাইটুকু আস্বাদন করিয়া দেখিয়াছিলেন এবং নিজেই স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন। সত্যই হাতে লাগিয়া থাকা জলসিক্ত ছাইয়ের আস্বাদ সুমিষ্ট গুড়ের মত!
তিনি উল্লাসে অধীর হইয়া উঠিয়াছিলেন। আসিতেছে, সিদ্ধি আসিতেছে!
এই সময়েই প্রভাত হইতেছিল। সেই প্রভাতেই তিনি বনের বাহির হইতে তারা হাড়ি এবং শিবে বাগ্দীর ডাক শুনিতে পাইয়াছিলেন। সোমেশ্বর রায় নৌকা পাঠাইয়াছেন তাঁহাদের ওপারে লইয়া যাইবার জন্য।
সুলতা এবার আর বাধা না দিয়ে থাকতে পারলে না। বললে—এই আমাকে বিশ্বাস করতে বলছ?
সুরেশ্বর বললে-আমি কিছুই বলছি না সুলতা। মহেশচন্দ্রের চিঠিতে যা লেখা আছে, তাই তোমাকে পড়ে শোনাচ্ছি। এর প্রমাণ তো আমি দিতে পারব না। সেকালে যা ঘটত, তা একালে হয়তো ঘটে না। কিংবা কেউ ঘটাতে চায় না বলে ঘটে না। মহেশচন্দ্রও সেই কথা লিখেছেন। শোন।
“এই বৃত্তান্ত শ্যামাকান্ত যখন বলিয়াছিলেন, তখন আমি বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলাম না। কিন্তু অবিশ্বাসই বা কি করিয়া করিব, তাঁহার সহিত প্রথম সাক্ষাতের দিনই তিনি আমাকে তাঁহার ধুনির ছাই খাইতে দিয়াছিলেন। আমি প্রথমটা খাই নাই। কিন্তু অপর সকলে খাইয়াছিল; তাহা দেখিয়া মুখে কিছুটা আস্বাদন করিয়া দেখিয়াছিলাম, সত্যই তাহার স্বাদ গুড়ের মত। শুধু তাহাই নয়, ইহার পরে কয়েকদিনই জলে নিজের হাত ডুবাইয়া আমাকে খাইতে দিয়াছেন, তাহাও সরবৎ বলিয়া মনে হইয়াছে। অবিশ্বাস করিব কি করিয়া?
এরপর বর্ষার সময় শ্যামাকান্তকে বাধ্য হয়ে থাকতে হয়েছিল কাঁসাইয়ের এপারে কীর্তিহাটে। বর্ষাবাদলের জন্য আচ্ছাদন ছিল, কিন্তু বন্যা প্রতিরোধের উপায় ছিল না।
সোমেশ্বর বলেছিলেন- দেখুন, ঝড়-বাদল-বান-এর উপর তো হাত নেই। তার উপর জঙ্গলে বান ঢুকলে সাপখোপ, পোকা-মাকড়ের উপদ্রব সে তো নিবারণ করা যাবে না। আসছে বছর আমি জঙ্গলটার চারিপাশে উঁচু পগার দিয়ে দেব। ঘরগুলোকে ভেঙে খুব উঁচু করে দাওয়া তৈরী করিয়ে দেব। ততদিন এ-পারেই থাকুন, একেবারে নদীর কিনারায়—কিনারাটা যেখানে খুব উঁচু। পাথরে কাঁকড়ের শক্ত পাড়, ওখানে আমাদের একখানা ঘরও আছে। বাগানবাড়ী করব বলে করেছি। পিছনে নদীতে একটা দহ আছে। ও-বাড়ীতে আমরা কেউ বাসও করিনি। ওখানেই থাকুন নির্জনে। তারপর বর্ষা যাক, তখন আবার—।
শ্যামাকান্তের কিন্তু বিলম্ব সহ্য হচ্ছিল না। তিনি পেয়েছেন, তিনি মনে মনে জপ আর যোগিনীকে স্মরণ করে ধুলো-মাটি যাই তুলুন তা মিষ্টি হয়ে যায়। জলে হাত দিয়ে ইচ্ছে করলে জল সরবৎ হচ্ছে, সিদ্ধি এসেছে; তিনি বুঝতে পারছেন, এই সাধনায় ছেদ না ফেলে পঞ্চ পর্বে পর্বে ওই সিদ্ধাসনে আসন করে বসে জপ-ধ্যান-হোমক্রিয়ার আকর্ষণে টানলে পূর্ণ সিদ্ধিকে আসতেই হবে। সর্বশক্তির মূল শক্তি আসবেন, এসে সামনে দাঁড়াবেন, বলবেন বর নে। জ্যোতির্ময়ী নিবিড় কৃষ্ণ জ্যোতিলেখা।
কি বর চাইবেন? তিনি জানেন, দেবী বলবেন- রাজ্য সম্পদ, দেবত্ব, দেবকন্যা —বল কি চাই?
শ্যামাকান্ত মহেশচন্দ্রকে বলেছিলেন—ভুলবার পাত্র শ্যামাকান্ত নয়। সে-সবে ভুলবেন না। তিনি বললেন-না-না-না-না।
—তবে অমরত্ব?
—উহু-উঁহু—
—তবে?
—শুধু তোমাকে, শুধু তোমাকে চাই। আর কিছু চাই না।
পাগল হয়ে উঠতেন যখনই বলতেন এ-কথা। তাঁর ঝাঁকড়া চুল দিয়ে মাথা নেড়ে গান গেয়ে উঠতেন।
আর কিছু বাসনা নাই (আমার)—
চাই না মোক্ষ চাই না মুক্তি
শুধুই তোকে পেতে চাই।
চাই না আমি অমরত্ব
সোনাদানা কি রাজত্ব—
তোর ওপর কায়েমী স্বত্ব
জবরদখল যেন পাই।
একাকার হতে চাইরে বেটা, তার সঙ্গে একাকার। বুঝলি! মাগ-ভাতারের মত। হা-হা। হা-হা। হা-হা।
সঙ্গে সঙ্গে দুলতে থাকতেন।
মহেশচন্দ্র লিখছেন সুলতা—তিনি শিউরে উঠেছিলেন শুনে। শ্যামাকান্তকে তিরস্কার করে বলেছিলেন—তোমার আস্পর্ধা তো কম নয়? কি বলছ তুমি?
হা-হা শব্দে অট্ট হেসে শ্যামাকান্ত যেন ভেঙে পড়তেন। মহেশচন্দ্র লিখেছেন—তিনি একদিন বলেছিলেন—তুমি কি?
—কি?
—পিশাচ?
—ধুর বেটা! আমি শিব রে, আমি শিব!
স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন মহেশচন্দ্র। নির্বাক হয়ে এই লোকটির দিকে তাকিয়ে ছিলেন। সুন্দর সুপুরুষ মানুষ, এমন কণ্ঠস্বর, যে-লোক গান গেয়ে কাঁদে, তাঁর সঙ্গে এমন প্রেমের সঙ্গে ব্যবহার, সে এমন পৈশাচিক কামনা কেমন করে পোষণ করে! কি জঘন্য কামনা!
শ্যামাকান্ত বলেছিলেন—ওরে বেটা, তন্ত্র না জানলে জানবি নারে। তন্ত্র না জানলে বুঝবি না। যে সাধক, সে শিব। শোন, শোন–
অনিত্য কর্মসংত্যাগী নিত্যানুষ্ঠান তৎপরঃ। মন্ত্রারাধনমাত্রেণ শিবভাবেন তৎপরঃ।
স্ত্রী ময়ঞ্চ জগৎ সর্বং তথাত্মানঞ্চ ভাবয়েৎ। হাঁ, ওরে বেটা, সাধকই একা শিবপুরুষ। বাকী ব্রহ্মাবিষ্ণু-ইন্দ্র-চন্দ্র-সূর্য-বায়ু-বরুণ-জগৎ-সংসার সব স্ত্রী। সব স্ত্রী। হাঁ!
সেইভাবে ভাবিত তখন শ্যামাকান্ত। ভাব তখন শুধু আর ভাবনায় নেই, তখন চেহারা নিচ্ছে। অন্ততঃ তিনি তাই ভেবেছিলেন। ওই ধুলো-ছাই যখন গুড় হয়েছে, তখন মধুর স্বাদ পেয়েছেন। সেই মধুর ভাণ্ডার পেতে বিলম্ব আর সইছিল না। ভরা কংসাবতীকে তিনি অভিশাপ দিতেন—তুই শুকিয়ে যাবি, তুই শুকিয়ে যাবি। সূর্যের তেজে তোর বুক পুড়ে যাবে, ঝলসে যাবে। চড়া পড়বে। মজে যাবি। ওই চাষীরা তোর বুকে লাঙলের ফাল চালাবে।
আকাশ মেঘকে অভিসম্পাত দিতেন। দিনের মধ্যে কয়েকবার আসতেন কালীমন্দিরে। এসে মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে দেবীমূর্তিকে গালাগাল করতেন। মধ্যে মধ্যে আক্রোশ পড়ত তাঁর নিজের সৌভাগ্যশিলার উপর। তাকে গালাগাল করে বলতেন—রাজবাড়িতে রাজভোগ খেয়ে তুই মজায় আছিস, নয়? রাজার মন যোগাচ্ছিস। কই দে আমার যা চাই, দে। তোকে আমি ভাঙব। ঠুকে ঠুকে ভাঙব। কমা-কাঁসাইয়ের জল কমা!
লোকজনেরা শঙ্কিতবিস্ময়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকত। মধ্যে মধ্যে রামব্রহ্ম তাঁর সঙ্গে তর্ক করতেন। বলতেন-এ হয় না, এ হয় না। বীরাচার তুমি ছাড়। নইলে মঙ্গল হবে না তোমার। প্রহার খাবে। বজ্রের প্রহার হবে। তন্ত্র আমিও জানি, আমি কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের বংশধর। এ-পথ তুমি ছাড়।
শ্যামাকান্ত অট্টহাস্য করতেন।
ওদিকে সেই পাগলিনীরও একটা পরিবর্তন হয়েছিল। সেই কীর্তিহাট গ্রামের মধ্যে এসে মানুষজনের সঙ্গে মিশতে চাইত কিন্তু মানুষজনে তাকে ভয় করত। মেয়েটা তখন আর একরকম। শ্যামাকান্তের নিষ্ঠুর পীড়ন সে সইতে পারত না, সুযোগ পেলেই ছুটে পালিয়ে আসত রায়বাড়ীতে। রাজকুমারী রাণী কাত্যায়নীর কাছে গিয়ে শান্ত মেয়েটির মত বসে বলত —একবার খুকীকে দাও না গো! একটু কোলে নিই!
দিতে ইচ্ছা না থাকলেও দিতে হত, ভয় করে দিতেন শিশু বিমলাকে তার কোলে। সে তাকে আদর করত। কিছুক্ষণ পর বিমলাকে নামিয়ে দিয়ে চলে যেত সোমেশ্বরের কাছে। ঘুরে বেড়াত ঘরময়। দেখে বেড়াত ঐশ্বর্য। অবাক হয়ে দেখত।
এরই মধ্যে একটা ঘটনা ঘটল। সেপ্টেম্বর মাস—আশ্বিনের প্রথম। ১২ই আশ্বিন, ২৮শে সেপ্টেম্বর মেদিনীপুরে কালেক্টারী রেভেন্যু দাখিল করতে গিয়ে নায়েব একটা লাট নীলামে ডেকে এলেন। পরগণা মাজনামুঠার সবথেকে বড় লাট—লাট মহাতাপপুর। মুনাফা সাত হাজার টাকা।
তখন মাস মাস রেভেন্যু দেবার আইন। মাসে-মাসে নির্দিষ্ট দিনে টাকা না দিতে পারলে sunset law অনুযায়ী নীলাম হয়ে যেত। সোমেশ্বর রায় মেদিনীপুরে একটা সেরেস্তা খুলেছিলেন। মামলা চালাবার জন্যে আর নীলামে সম্পত্তি ডাকবার জন্যে। ভাল মহল সচরাচর জমিদারেরা ছাড়তেন না, লোকসানি মহল নীলাম হত। ছোট মহল ছেড়ে দিতেন, ছাড়া নীলাম হতে দিতেন না। এবার ভাল মহল উৎকৃষ্ট সম্পত্তি পাওয়া গেছে। খাঁটি সোনা।
রায়বাড়ীর কালীমন্দিরে ঢাক-ছোল বেজে উঠেছিল। তার সঙ্গে শিঙা শানাই। ষোড়শো- পচারে আনন্দময়ীর পূজার ব্যবস্থা হয়েছিল। তার সঙ্গে সৌভাগ্যশিলা রাজরাজেশ্বর পুজা। সোনার বেলপাতা, সোনার তুলসী গড়বার হুকুম হয়েছিল সেকরাকে। গ্রামে তখন স্বর্ণকার এনে বসানো হয়েছে। তার সব থেকে বড় কাজই ছিল এই।
একদিন পর মহালয়া—পিতৃপক্ষের একাদশী। সেদিন বলি দিয়ে পূজা হবে। ব্রাহ্মণভোজন হবে ব্যবস্থা হচ্ছে, এরই মধ্যে এসে দাঁড়ালেন শ্যামাকান্ত। চোখদুটো লাল হয়ে উঠেছে। ক্রোধে ফেটে পড়ছেন।
বললেন—রায়বাবু, আমার শিলা দাও।
—কি হল? সোমেশ্বর চমকে উঠে প্রশ্ন করেছিলেন।
সেই যে যোগিনী অভিষেকের দিন শ্যামাকান্ত রামব্রহ্ম ন্যায়রত্নকে বলেছিলেন—ওই পূজাটা তুমি সেরে দিয়ো হে ন্যায়রত্ন। তারপর থেকে ন্যায়রত্নই পূজা করে আসছেন। শ্যামাকান্ত বলতে গেলে কীর্তিহাটেই আর বড় আসতেন না। ওখানেই থাকতেন। সোমেশ্বর ভেবেছিলেন—তান্ত্রিক ভুলেই গেছে নারায়ণশিলার কথা। মধ্যে মধ্যে এসে গালাগাল দিয়ে যেতেন শিলাকে, ব্যস ওই পর্যন্ত।
শ্যামাকান্ত বলেছিলেন-আমি চলে যাব হে। এখানে হ’ল না। ভাল আমার হ’ল না। ভাল হল তোমার। আমার সাধনার ফল তুমি পাচ্ছ। আমাকে চলে যেতে হবে।
—কেন? আপনি তো পেয়েছেন। আজ ধুলো-মাটি আপনি হাতে করতে গুড় হয়, ভূরো হয়—
—দুর শালা, গুড় তৈরী করতে পারলেই যদি সিদ্ধি হয়, তবে তো আখের চাষ করলেই তা হত রায়বাবু। তোমার মত টাকা থাকলে, জমিদারী থাকলে তো লাখ মণ গুড় কিনে রাখলেই সিদ্ধি ঘরে বন্ধ করে রাখতে পারা যায় হে। শালা গুড়ের ব্যবসাদাররা তো তাহ’লে সিদ্ধপুরুষ!
তারপর মাথার চুল টানতে টানতে বলেছিলেন—মাসে মাসে পঞ্চপর্ব চলে যাচ্ছে, ঘরে বসে ভেরেণ্ডা ভাজছি, যোগিনীছুড়ির মন উড়ি-উড়ি করছে। সাধন নইলে পালায়।
—কোথা পালাবে? আমার এলাকায়—
হা-হা করে হেসে বলেছিলেন—ওরে শালা, শালুক চিনেছ গোপালঠাকুর, ওরে, দেহে তো ও একটা পাগলী রে, পাগলীটা এল সেদিন —যোগিনী ঘুরছিল, আমার টানে ওর মধ্যে ঢুকল। সাধনের টানে বাঁধা ছিল। না-না, আমি চলে যাব, আমি চলে যাব। তোমার ঘরে লক্ষ্মী ওথলাচ্ছে, তুমি শালা মজা মারছ। ওই নুড়িটা ঢালছে তোমাকে। চলে যাব আমি। পরশু মহালয়া, কাল চতুর্দশী, তিথি চলে যাচ্ছে, পর্ব পালাচ্ছে, এপারে বসে বান দেখছি আমি। জান, ওপারে রাত্রে লগ্নযোগ আমাকে মুখ ভ্যাঙচায়। শেয়ালগুলো হি-হি করে হাসে। ঘরে বসে জপ করি, আমার জপ কেটে যায়।
হঠাৎ সোমেশ্বর বললেন—বেশ তো। বসে থাকতে হবে না আপনাকে। আগে এ-কথা বললে নিশ্চয় আমি ব্যবস্থা করতাম। চলুন, নৌকো করে নিয়ে যাব আমি। আমি শিবে, তারা যেমন যাই, তেমনি যাব। করুন সাধন আপনি।
শ্যামাকান্ত বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে সোমেশ্বরের হাত চেপে ধরেছিলেন।
—যাবে? না তখন বলবে—এই বানে যাওয়া যায়, আপনি বলুন! না-হয় বলবে- আপনি যান, আমি যেতে পারব না। তোমরা বড়লোক। সিংদরজায় খিল দেবে। পাহারাদারে পাহারা দেবে। বলবে—ভাগো!
—না, তা বলব না।
—তিন সত্যি কর। বল যাব—
—যাব, যাব, যাব।
সুরেশ্বর বললে–সুলতা, এরপর যা ঘটেছিল, তা জানত সবাই। নৌকোডুবি হয়েছিল। ভেসে গিয়েছিলেন শ্যামাকান্ত। সোমেশ্বরও ভেসে যাচ্ছিলেন, তাঁকে যারা বাঁচিয়েছে তারা হাড়ি। শিবু বাগ্দী নাগাল পেয়েছিল মনোহরার, শ্যামাকান্তকে কেউ ধরতে পারেনি। কেউ যেন তার বুকে চেপে কি জলের নীচে থেকে পায়ে ধরে টেনে তাকে ডুবিয়ে নিয়ে কোথায় জলস্রোতের টানে টেনে নিয়ে গিয়েছিল, তার হদিস কেউ পায়নি।
তাঁরা প্রাণে বেঁচে কোন রকমে ওপারে উঠে রাত্রি কাটিয়ে পরদিন এপার থেকে নৌকো আনিয়ে ফিরেছিলেন। সোমেশ্বর রায়ের যে দেহে আতর মাখতেন—সাবান মাখতেন তাঁর সেই সারা অঙ্গে কাদা কাদা আর কাদা। শিবু তারা কাদায় মাখামাখি। যোগিনী মেয়েটার একরাশ রুক্ষ চুল কাদায় বীভৎস দেখাচ্ছিল। সারা গায়ে কাপড়ে কাদা। বিবরণ শুনে লোকে স্তম্ভিত হয়েছিল। রামব্রহ্ম ন্যায়রত্ন বলেছিলেন—মহাশক্তি! এ মহাশক্তির রোষ! বামাচারীরা এইভাবে অপঘাতে মরে—নয় উন্মাদ হয়ে যায়।
লোকটিকে তো মা সাধনের উপকরণ দিয়ে পাঠিয়েছিলেন। এমন কণ্ঠ, এমন সংগীতবোধ, কোনদিন মা বলে ডেকে গান গাইলে না। হায়রে—
তোর উপর কায়েমী স্বত্বের দেখব দখল, পাই কি না-পাই! দেখিয়ে দিয়ে গেল বাবা!
শিবু বাগ্দীকে সোমেশ্বর পাঠিয়েছিলেন কিনারা ধরে খুঁজতে, যদি শ্যামাকান্তের দেহ পাওয়া যায়। কিন্তু পাওয়া যায়নি। পাওয়া যায়নি নয়, শিবু আর ফেরেইনি। পাওয়ার কথা নয়, কাঁসাই নদী উপরে এমনি পাহাড়ে নদী। বারো মাসের ছ’মাস হেঁটে পার হওয়া যায় কিন্তু নীচে কাঁসাই হয়েছে হলদী। কংসাবতী হয়েছে হরিদ্রাঙ্গী। ভাগীরথীর সঙ্গে যেখানে মিশেছে, তার একটু উপরে তার সঙ্গে মিশেছে এসে কেলেঘাই। সে এক বন্যাবর্বরা আদিবাসিনীর মত দুর্মদা। ওই মনোহরার মতই সে পাগলী। হলদীর পরই ক্রোশ কয়েক দক্ষিণে রসুলপুরের মোহনা।
বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলার রসুলপুরের মোহনা সুলতা! বঙ্কিমচন্দ্র এখানে কাপালিককে দেখেছিলেন। তার কাল, শ্যামাকান্তের কাল থেকে অনেক পরে। ১৮২২/২৩ সাল আর ১৮৭২ সাল বোধ হয়। পঞ্চাশ বছর পর।
যাক, কোন্ কথা থেকে কোন্ কথায় এলাম। বলছিলাম হলদীর কথা। সমুদ্র থেকে জোয়ার উঠে ভাগীরথীর বুক বেয়ে চলে যায় চুঁচড়োর ধার পর্যন্ত। আশেপাশে যেসব নদী-খাল এসে পড়েছে এর মধ্যে, তার মধ্যে দিয়েও জোয়ার ঢোকে। হলদীতে জোয়ার ঢোকে। বর্ষার সময় তাই কাঁসাই যখন ভরে, তখন সে তরঙ্গময়ী হয়ে ওঠে। যেদিন শ্যামাকান্ত ডোবেন, সেদিন ছিল আশ্বিনের কৃষ্ণা-চতুর্দশী। আজও আশ্বিনের চতুর্দশী অমাবস্যা-পূর্ণিমার জোয়ারকে বলে ষাঁড়াঘাঁড়ির বান। অমাবস্যার জোয়ারই প্রবল, সেইটেই ষাঁড়ার বান। জোয়ারের পর যখন ভাটার টান পড়ে, তখন তার টানও ভয়ঙ্কর। সেই টানে ভেসে গিয়েছিলেন শ্যামাকান্ত। তাঁকে পাওয়ার কথা নয়। তাছাড়া যত বীভৎসই মনে হোক তাঁর আচরণ, সাধনভজন, তবু তাঁকে কেউ অস্বীকার করতে পারেনি। তাঁর দেহ গঙ্গায় পড়ে গঙ্গাসাগর সঙ্গমে পড়েছে। মহামায়া তাঁর দুর্নিবার ভয়ঙ্কর বাসনাকে ওই সঙ্গমতীর্থে সমাধিস্থ করে তাকে মুক্তি দিয়েছেন—এই ধারণাই নিঃসন্দেহে করেছিল লোকে।
এ ব্যাখ্যা করেছিলেন রামব্রহ্ম ন্যায়রত্ন।
সোমেশ্বর অনেক হায় হায় করেছিলেন। শ্যামাকাণ্ডের শ্বশুরবাড়ীতে একটা খবরও পাঠিয়েছিলেন। তখন শ্যামাকান্তের স্ত্রীও বিগত। থাকবার মধ্যে ছিলেন শাশুড়ী। আর বছর- দুয়েকের ছেলে বিমলাকান্ত। তাঁদের সাহায্যও কিছু করতে চেয়েছিলেন সোমেশ্বর, কিন্তু তাঁরা তা নেননি; ভট্টচাজের ঘর হলেও, লাখরাজ মানে জমি তাঁদের যথেষ্ট ছিল। একশো বিঘার জোত, সে সামান্য নয়, তাছাড়া শিষ্য ছিল অনেক। পদ্মনাভ ভটচাজ-গৃহিণী তখন গুরু-মা হিসেবে দীক্ষা দেওয়ার কাজ চালিয়ে যেতেন। মানে-সম্মানে তাঁরা বৃহৎ ছিলেন না কিন্তু মহৎ ছিলেন। হেসেই বলেছিলেন-না। মায়ের কৃপায়, নারায়ণের দয়ায় চলে যাবে। তবে যদি খবরটা আগে দিতেন, তাহলে ভাল হত, একবার বিমলাকান্তকে নিয়ে তার কাছে গিয়ে দেখতাম। তা দোষ রায়বাবুকেই বা কি দেব, দোষ অদৃষ্টের, আর কর্মফেরের। যা হয়েছে তা মায়েরই ইচ্ছে আর তাঁর কর্মফল। তার সঙ্গে আমাদের অদৃষ্টের।
সোমেশ্বর রায় নিজে একটি প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন। ওই সাধককে তিনি বাঁচাতে পারেননি তার জন্যও বটে, আর তিনি একরকম তাঁর শিষ্য—উত্তরসাধক হিসেবে সেজন্যেও বটে। এ না করে তাঁর মন তৃপ্তি পায়নি। এর বিধান দিয়েছিলেন রামব্রহ্ম ন্যায়রত্ন। ব্রাহ্মণভোজন করিয়েছিলেন। এখান ওখান থেকে তান্ত্রিক কৌল প্রভৃতিদের এনে সমাদর করে ভোজন- বিদায়-তাও করেছিলেন। তার সঙ্গে কাঙালীভোজন। আর ওই কাঁসাইয়ের পাড়ে যে বাগান, সেই বাগানে, অনেক যত্ন করে রেখেছিলেন শ্যামাকান্তের ওই মনোহরা যোগিনীকে। দাসী পর্যন্ত রেখে দিয়েছিলেন। আরও কিছু করেছিলেন সোমেশ্বর, তিনি নিজে এবার তন্ত্রমতে পূজা-অর্চনায় গভীরভাবে মন দিয়েছিলেন।
আশ্চর্যের কথা, যোগিনী মেয়েটা শ্যামাকান্তের নিখোঁজের পর শান্ত হয়ে গিয়েছিল-বিশেষ ক’রে রায়বাবুর মেয়ে বিমলাকে নিয়ে তার আর মমতার শেষ ছিল না। এবং শিশু বিমলাও তার কোল এত ভালবাসত যে তাকে না পেলেই সে কাঁদতে আরম্ভ করত।
কিছুকাল পর সোমেশ্বর তাকে নিয়ে সাধনার চেষ্টাও করেছিলেন। কিন্তু রামব্রহ্ম ন্যায়রত্ন সাবধান করে দিয়েছিলেন তাঁকে। না—এ ঠিক হবে না বাবু। এ করবেন না।
শ্যামাকান্ত মহেশচন্দ্রকে বলেছিলেন—নৌকো ওল্টায় নি মহেশ! সোমেশ্বর রায় আমাকে নৌকো থেকে মাঝ কাঁসাইয়ের সেই ষাঁড়া কোটালের ভাটির টানের সময় তখন–তখন তুলে ফেলে দিলে। দিলে তারা হাড়ি।
আমি ভাবনায় ডুবে ছিলাম। মনে মনে ভাবছিলাম কি জানিস—ভাবছিলাম আজ কি হবে? আজ গিয়ে বসব আসনে। যোগিনীর কাপড়ের খুঁটে আমার গেরুয়ার খুঁট বেঁধে বসব। ডুবব। বুঝলি—রামপ্রসাদের গানে আছে—’ডুব দে রে মন কালী বলে।’ তাই ডুবব। জগৎ সংসার সব মুছে যাবে। শব্দ না গন্ধ না স্পর্শ না—কিছু থাকবে না। বাইরে হোক প্রলয়, আমার কাছে কিছু থাকবে না। হাঁ। আমি আর আমার সামনে অন্ধকার। যোগিনী অজ্ঞানের মত বসে থাকবে। তারপর অন্ধকারের মধ্যে আলো-হাঁ আলো-নীল আলো—মহামেঘ-প্রভার মতো আলো। চমকে চমকে উঠবে। কলরব করবে শিবারা—হোমের আগুনে আহুতি দেব এক এক কুশী। এই সব ভাবছি। আর ভাবছি—আজ যাবে কোথা? হুঁহুঁ! জানিস, মনের মধ্যে গানের কলি এসেছিল, সে এক কলি আজও মনে রয়েছে রে-’আর তুই পালাবি কোথা?” হঠাৎ তারা হাড়ি উঠে এসে আমাকে জাপটে ধরে চ্যাঙদোলা করে তুলে ঝপ করে জলে ফেলে দিলে। রায়বাবুর মুখ দেখি নি। শুধু শুনেছিলাম তার কথা। যাও—সিদ্ধি তোমার জলের তলায় আছে। সৌভাগ্যশিলা নেবে তুমি! যাও!
আমি ডুবে গেলাম। সাঁতার জানতাম—তা ভালই জানতাম। কালীঘাটে জোয়ারের টান থেকে দাঁতে কাপড় কামড়ে ধরে সেই মাগীর শব টেনে এনেছিলাম। কিন্তু কাঁসাই সেদিন ভীষণ। টেনে নিয়ে চলল। ভেসে উঠলাম তবু। উঠে সাঁতার কেটে নৌকোটা ধরতে গেলাম। তো রায়বাবু একটা দাঁড় কেড়ে নিয়ে মাথায় মারলে। এই দেখ কপালের দাগ। এই খানিকটা লেগেছিল, তাতেই কপাল ফেটে গেল। গোটাটা মাথায় পড়লে মরেই যেতাম।
তা মরে গেলাম না, সব কালো হয়ে গেল। ভারী আনন্দ হ’ল রে। ভারী আনন্দ মনে হ’ল, সেই কালো রে। যে কালোর মধ্যে ডুবব ভাবছিলাম! কালী কালী বল মন—মনে হ’ল কালীর মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছি। আসছে-সে আসছে। বাসরায় শালাকে শাপশাপান্ত করলাম না, করতে ভুলে গেলাম। নাক দিয়ে মুখ দিয়ে জল ঢুকছিল—আপনা-আপনি কুম্ভক করে চিৎ হয়ে মড়ার মত ভাসলাম। মনে হল কে যেন কোলে করলে।
তাঃ, না—। সেটা আমার ভুল। বুঝলি, কোলে কেউ করেনি, একটা শালগাছের গদি ভেসে যাচ্ছিল—সেই গদিতে গিয়ে ঠেক খেয়েছিলাম। কি ক’রে যে গদিটার ওপরে উঠে শুয়েছিলাম তা জানি না। করাতীরা গদিটা চৌকো করে চিরে রেখেছিল। উপরের পিঠটাতে শুয়েছিলাম শালা অনন্তশয্যেতে বিষ্ণু ঠাকুরের মত। দিব্যি ভাসতে ভাসতে এসে লেগেছিলাম একটা বাঁকের মাথায় চড়াতে।
গাঁয়ের লোকেরা নদীর ধারে এসে কাঠ সমেত আমাকে তুলেছিল।
কপাল। আর সেই মাগীর ছলা। মাগীর ওই কাজ; প্রহার খেয়েও ছাড়বে না—তাকেই ধরা দেয়!
চেতনা হয়েছিল দুপুরবেলা। দেখি সব বাগদী আর মুসলমান। আর কেরেস্তান। সে এক তিনদিকে জল—একটা দ্বীপের মতন আশ্চর্য জায়গা—বামুন-কায়েতের বংশ নেই। জায়গাটার মালিক মুসলমান হাজী সাহেব। হাজীও বটে ঠাকুরও বটে। তাকে চিনলাম—তারা আমার শ্বশুরবাড়ী শ্যামনগরের মালিক ছিল। তার আগে ব্রাহ্মণ ছিল। মস্ত যোগীর বংশ। ঠাকুর উপাধি ছিল। এরা তারাই।
তারাই বাঁচালে।
ঠাকুর মিঞা শ্যামাকান্তকে খুব খাতির করেছিলেন। তিনি তাঁকে চিনলেও নিজের পরিচয় তাঁকে দেন নি। ঠাকুর মিঞা পিতৃপুরুষের যোগবিদ্যা আর গণনাবিদ্যা ছাড়েন নি। তিনি নিজে হাজী ধার্মিক লোকও বটেন তার সঙ্গে আমীরও বটেন। নানকার গ্রামখানায় তাঁর শাসন অদ্ভুত। কেউ কারুর জাত মারে না। মারবার হুকুম নেই। মুসলমানদের প্রতাপ বেশী বটে কিন্তু অন্য জাতের মেয়েকে কেউ সহজে মুসলমান ক’রে কেড়ে আনতে পারে না। বলে—উটি চলবে নাই। উঁহু! তিনি শ্যামাকান্তকে তান্ত্রিক বলে চিনতে ভুল করেন নি। বলেছিলেন—তা তুমি থাক গোসাঁই, ঢাক ঢোল বাজায়ো নাই, চুপচাপ ওই গাঁয়ের ধারে বাগ্দীদের কালীর থান আছে, সেখানে থাক।
গ্রামের কালীর স্থান একেবারে শ্মশানের ধারে। স্থানটি পছন্দ হয়েছিল তাঁর। বসেও ছিলেন কিছুদিন। মাস কয়েক। মাটির কালীমূর্তি তৈরী করে নতুন করে আসন করবার চেষ্টায় ছিলেন। ঠাকুর মিঞা একদিন তাকে ডেকে বলেছিলেন—তুমি নাকি, ইয়ারা বলছে, খুব ভাল গান কর গোসাঁই!
শ্যামাকান্ত বলেছিলেন—তা কিছু জানি।
গানবাজনার মধ্যে তাঁর সঙ্গে আলাপ জমেছিল। তিনি গাইতেন ঠাকুরসাহেব নিজে বাজাতেন; তবে সে সব গান তাল মান লয়ের রাগরাগিণীর আলাপ। কিন্তু তবু মাসকয়েক পর ওখান থেকে চলে এসেছিলেন শ্যামাকান্ত। এসেছিলেন কামরূপ কামাখ্যা। সেও তাঁকে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন ওই ঠাকুরসাহেব।
শ্যামাকান্ত খুঁজেছিলেন নায়িকা। সাধন-সঙ্গিনী ভৈরবী। একদিন ঠাকুরসাহেবকে বলেছিলেন মনের কথা। ওখানে ঠাকুরসাহেবের কড়া নজর ছিল ওই বিষয়টিতে। মেয়ের ইজ্জত-ধর্ম—এ কেউ কারুর নাশ করতে পারবে না। দুষ্ট নষ্ট মেয়ে ছিল। কিন্তু সে গোপন রেখে চলত। প্রকাশ পেলে তিনি কঠিন সাজা দিতেন। সেই জেনেই শ্যামাকান্ত তাঁর কাছে অনুমতি চেয়েছিলেন। একটি ভৈরবী তিনি সংগ্রহ করে নেবেন বা বাইরে থেকে সংগ্রহ করে আনবেন। বলেছিলেন—ঠাকুরসাহেব, এই পথেই সাধন করে এসেছি। সাধন আমার এ পথ ছাড়া হবে না। আমাকে হুকুমটা দেন। আমার সিদ্ধি হ’লে আপনাকে আমি রাজা ক’রে দোব!
ঠাকুরসাহেব নিজের দাড়িতে হাত বুলিয়ে বলেছিলেন—সিদ্ধাই আমি জানি হে গোসাঁই। তা হাজার পথ থাকতি ই পথ নিলা ক্যানে হে? রসুল আল্লা, ই কি ফ্যারে পড়িছ হে! দেখ, তোমার ধরম তোমার। কিছু বলব না আমি। কিন্তু উটি ইখানে হবে নাই সো হুকুম নাই আমার বাপের হজরত গুলমহম্মদ ঠাকুরের। না।
একটু চুপ করে ভেবে নিয়ে বলেছিলেন-আমার একটা বাত শোনবা? তুমি কাউর কামাখ্যায় যাও হে! ই সাধন তোমার সিখান ছাড়া হবে নাই! আমি ইসবের কিছু জানি। ই দ্যাশে যারে তুমি সাধন কর হে সে মা সেজে বসে আছে। বুঝলা না! কাঁউর হ’ল ডাকিনীর দ্যাশ, কুহক-বিদ্যার চল সিখানে। তুমি সিখানে যাও। ইখানে উ হুকুম আমি দিব না বাপু! টাকা-কড়ি আমার কাছে কিছু লিবা আমি দিব। গাঙ দিয়া বড় বড় মালের ভাউলে যায়—গৌহাটী। আমার এই গোয়ানরা আছে। তারা এককালে হারমাদ ছিল। এখুনও ফাঁক পেলে মারতে পারে ভাউলে বারো। তা আমার শাসনে পারে না। দু-চারজনা ভাউলেতে কাম করে। তারা তোমাকে নিয়া গৌহাটী কামাখ্যা পৌঁছায় দিবে। বুঝলা? ইখানে উ সব হবে নাই। তুমাকে চলি যাতি হবে। ই হুকুমের লড়চড় নাই।
আসবার দিন ঠাকুরসাহেব শ্যামাকান্তকে নগদ একশো টাকা দিয়েছিলেন। আর বলে- ছিলেন—একটা বাত শোনবা? তুমার থেক্যা আমার উমর অনেক বেশী গোসাঁই। কত আর উমর হবে তুমার। পঁচিশ! আমার উমর ষাট পার হে! আর আমি বুঝি! আমরা তো হিদু ব্রাহ্মণ ছিলাম। সিদ্ধাই ছিল আমাদের। ঠাকুর নাম ঘুচে নাই। শুন, যা বলি শুন! নায়িকা ভৈরবী এ নিয়া সাধন কর না বাপ। বড় খারাপ। ই হ’ল কি জান—বুকে সাপ নিয়া দিল ঠাণ্ডা করা। ডংশন সে করবেই। তার থিকা এক কাম করিয়ো। পোলার মতুন মাকে ডাক। আর ওই পথে যদি হাঁটবা—তবে স্বজাত স্বঘর দেখে কন্যের লক্ষণ দেখে সাদী ক’রে পরিবার নিয়া সাধন কর। পথ সোজা হবে। বুঝলা! জান তো সব। আমি ইসলামের বান্দা, ইসব আমাদের কাছে কাফেরী। বেধরম অধরম। তবে আমার বাবা গোস্যা নাই। আমি জানি, আমি আমার ইসলামকে মানলেই হল। তবু খানিক আধেক বুঝি, বললাম- তুমি ভেব্যা দেখো! হাঁ?
শ্যামাকান্ত সেলাম ক’রে বলেছিল-ঠাকুরসাহেবের কথা মনে থাকবে আমার! সঙ্গে সঙ্গে হেসেছিলেন।
ঠাকুরসাহেব এবার শক্ত হয়ে উঠে বলেছিলেন—হাসিয়ো না পোলা, হাসিয়ো না। তোমার বুকে ডংশন আমি তোমার ললাটে দেখছি হে!
মহেশচন্দ্র লিখেছেন—আমি তোমাকে সব বিশদ করিয়াই বিবৃত করিলাম। যে দিবসে তিনি আমাকে তদীয় জীবনের ঘটনাবলী বিবৃত করিয়াছিলেন সে দিবস একটা গোটা বেলা কাটিয়া গিয়াছিল। আমি সমস্ত শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলাম। হিন্দুর সন্তান, এমত কাহিনী অনেক শুনিয়াছি। আমাদের অঞ্চলে এক কাপালিক আসিয়া কিছুদিন ছিল, তাহাকে দেখিয়া ভয় করিত। শুনিতাম সে নরমাংস খায়, নরবলি প্রদান করে। শ্যামাকান্ত- সেই ধরনের মানুষ—ওই এমনি এক পথের পথিক। অথচ লোকটির কাহিনী শুনিয়া তাহার উপর ক্রোধ করিতে পারি নাই। তাহার একটা আকর্ষণী ছিল এবং কোথায় যেন একটা দুঃখী ভাব ছিল। আমি তাহার কথাগুলি সেই রাত্রে গৃহে প্রত্যাবর্তন করতঃ সব লিখিয়া রাখিয়াছিলাম।
ইহার দুই-চারিদিন পর তাঁহার নিকট গিয়া দেখিলাম, তিনি খুবই চঞ্চল—যেন তাঁহার পাগলামি আবার বৃদ্ধি পাইবে মনে হইল। গালাগালি দেওয়া বৃদ্ধি পাইয়াছে। পাণ্ডারা বলিলেন—সারাদিন আহার করেন নাই।
জিজ্ঞাসা করিলাম—আবার এসব কি হইতেছে?
সুরেশ্বর বললে—মহেশচন্দ্র মনে করেছিলেন গালাগাল দেবেন শ্যামাকান্ত। কিন্তু না। তিনি কেঁদে ফেলেছিলেন, বলেছিলেন—ওরে, কাল যে এক মহাপর্ব রে। পঞ্চপর্বের তিন পর্ব একসঙ্গে। সংক্রান্তি, কৃষ্ণ-চতুর্দশী তার উপর মঙ্গলবার। ওরে, এ পর্ব দুর্লভ। বড় দুর্লভ! পর্ব চলে যাবে, আমার সাধন হবে না রে আমার সাধন হবে না।
—বেশ তো, তুমি তোমার সাধন কর না। কে বারণ করছে?
ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে শ্যামাকান্ত বলেছিলেন—শির নাই তার শিরঃপীড়া! পাত্র নাই তার রন্ধন! ওরে বেটা, কাঠ নাই আগুন ধরবে কিসে রে?
মহেশচন্দ্র লিখেছিলেন—আচ্ছা বলতে পার, এই যে এমন করে কাদাধুলো মেখে বনে জঙ্গলে শ্মশানে এমনি ক’রে ঘুরছ, এই তো একবার একবার কেন দু-দুবার জলে ডুবতে ডুবতে বাঁচলে, তারপরও এমনি ক’রে ঘুরছ কেন, এতে হবে কি?
হবে কি? হবে কি? অবাক হয়ে গিয়েছিলেন শ্যামাকান্ত। তারপর বলেছিলেন—রাজা হয়ে কি হয় রে বেটা? টাকা জমিয়ে কি হয় রে? কি হয়? সোমেশ্বর রায় শালা জমিদার হয়েছে। জমিদারী কত, তবু কিনছে। কেন রে? সুখ রে বেটা, সুখ। ওরে জন্ম জন্ম ধরে মানুষ সুখ খুঁজছেই খুঁজছেই। আমি পরজন্ম খুঁজছি। ওই পেলে সব সুখ আমার হবে। সুখে ডুবে যাব রে! দুঃখ, বুঝলি, এই পাঁজরায় পাঁজরায় দুঃখ, সব সুখের মধ্যে মিলিয়ে যাবে। ওরে, এক একটা পর্বের লগ্ন যায়, সুখ মাথার ওপরে মেঘের মত গুড়গুড় ক’রে ডেকে চলে যায়। খানিকটা ছোঁয়া দিয়ে ডাকে। ওরে বর্ষায় না। একটু চুপ ক’রে থেকে বলেছিলেন—সোমেশ্বর রায় আমার সৌভাগ্যশিলা কেড়ে নিলে—জলে ফেলে দিলে, দিক; শাপ সাধককে দিতে নাই দোব না। শালা আমাকে বাঁচিয়েছে রে। জানিস শালা মহান ডাকাত, আমার মনে হত শালা সিদ্ধি হ’লে জমিদারই হব। হাতীতে চড়ব পাল্কীতে চড়ব ঘোড়াতে চড়ব—এই হুকুম দোব, বাঁধ শালাকে মার শালাকে! লোভ হচ্ছিল। তা বেশ করেছে। ও লোভটা গিয়েছে রে। কিন্তু দুঃখ তো যাওয়া চাই রে। সুখ তো চাই। ওই আ-কা-শ ভরা মেঘের মত সুখ! জানিস—আমার সব ঠিক। সব ঠিক। লক্ষণে বুঝতে পারছি। শুধু আমার নায়িকা চাই। পাচ্ছি না। জায়গা, আসন আমার মিলেছে! শুধু নায়িকা!
মধ্যে মধ্যে ক্ষেপে উঠতেন সৌভাগ্যশিলার উপর।
বলতেন—ওই, ওই নুড়ি ভগবানই আমার সর্বনাশ করেছে রে। বুঝলি, বৈষ্ণব সাধু আমাকে বলেছিল—সন্ন্যাসীর কাছে ও হল চৈতন্যশিলা। গৃহস্থের কাছে সৌভাগ্যশিলা- ধনসম্পদ ভূমি সৌভাগ্য দেয় আর সাধুকে দেয় চৈতন্য। চৈতন্য না কচু। ভেদ ভেদবুদ্ধি রে, ভেদবুদ্ধি। বুঝলি ওই মনোহরা যোগিনীকে আমি পেলাম, কিন্তু ওকে প্রকৃতি হিসেবে নিতে গিয়ে মনে হল কি জানিস? মনে হ’ল—পাপ হবে। কামার্থে গ্রহণ করা হবে। কাম! কাম কি রে? কাম তো মহাশক্তির বিধান। ওইখানে তো সৃষ্টি রে। পরমানন্দ। মেয়েটাকে দেবতা ক’রে পুজোই করলাম। বললাম—তুই আমার দুতী। দূতী! বুঝলি, এ ওই নুড়িটার খল! ব্রহ্মাণ্ডের রাজা দেবতাদের দেবতা, বেটা পালক! বৈকুণ্ঠে দরবার করে, জয় বিজয় পাহারা দেয়, রাজভোগ খায়। আর বলে এটা পাপ—ওটা পুণ্য। পাপ পুণ্য। থাক বেটা জমিদার-বাড়ীতে পুষ্যিপুত্তুর ঘরজামাইয়ের মত। খাক দাক আর মামলা বাধাক-পরের হরে নিয়ে দিক সব চুটিয়ে দিক—ওই রায়কে।
ওঃ, ওটাকে ভেঙে চুরমার করে দিয়ে আসতে পারতাম! শালা সোমেশ্বর থাক—ওই ওকে নিয়ে থাক। মামলা করুক, মকদ্দমা করুক, টাকা করুক। চাই না। আমার নায়িকা চাই। এই কামাখ্যা পীঠ!
নায়িকা পান নি। পান নি-না—তাঁর নিজের চোখে কাউকে নায়িকা বলে মনে হয় নি –এ শুধু তিনিই জানেন।
তার কারণ মহেশচন্দ্র লিখেছেন-নায়িকা নায়িকা ক’রে আক্ষেপ করতেন, ওখানকার পাণ্ডাদের মধ্যে তান্ত্রিক বলতে গেলে সবাই। তাঁদের মধ্যে দু-চারজন বামাচারী বীরাচারীও ছিলেন, তাঁরা তাঁকে নায়িকা সংগ্রহে সাহায্য করতে গিয়েছিলেন। কামাখ্যা অঞ্চল নাকি ডাকিনীতন্ত্রের দেশ, ডাকিনীবিদ্যা জানা নায়িকা তাঁরা এনে দিয়েছেন তাঁকে, কিন্তু তিনি বলেছেন—ও না। না-না-না। এতে হবে না। আমার মন চাচ্ছে না। লক্ষণ ওর যতই থাক।
হঠাৎ একদিন একটা ঘটনা ঘটল।
শ্যামাকান্ত মন্দিরের চত্বরে ধ্যানে বসেছিলেন রাত্রে। গৌহাটী অঞ্চলে শহরের মধ্যেই বাঘ ঢুকত তখন। কামাখ্যা পাহাড়ে নিত্য রাত্রে বাঘের ডাক শোনা যেত। পাণ্ডারা সন্ধ্যার আগেই মন্দির বন্ধ করে চলে আসতেন। সে দিন ছিল শুক্লা চতুর্দশী। শ্যামাকান্ত সন্ধ্যার সময় গিয়ে মন্দির-চত্বরে ঢুকেছিলেন—রাত্রে ক্রিয়া করবেন। কারুর বারণ তিনি শোনেন নি। নায়িকা না নিয়েই বসেছিলেন।
সকালে মন্দির-চত্বরে পাণ্ডারা ঢুকে দেখলে তাঁর আসনে তিনি তখনও ধ্যানস্থ হয়ে বসে। হাতে তাঁর যন্ত্রপুষ্পের অঞ্জলি। জবা অপরাজিতা বিশ্বপত্র।
পাণ্ডারা প্রথমটা ভেবেছিল সমাধিস্থ হয়েছেন বুঝি। কিন্তু না। পাণ্ডাদের সাড়াতেই চোখ মেলে দিনের আলো দেখে অঞ্জলি তাঁর যন্ত্র আঁকা পীঠে ঢেলে দিয়ে নিজের হাত শুঁকেছিলেন। মুখ তাঁর উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। এই অঞ্জলি দেওয়া ফুলের কয়েকটা ফুল তুলে পাণ্ডার হাতে দিয়ে বলেছিলেন—দেখ তো শুঁকে! দেখ তো!
বিস্মিত পাণ্ডা প্রশ্ন করেছিল—শুঁকে?
—হ্যাঁ-হ্যাঁ। সুগন্ধ পাচ্ছ কি না দেখ তো!
—তা তো এখান থেকেই পাচ্ছি।
ব্যঙ্গ করে হেসে বলেছিলেন শ্যামাকান্ত —তা তো পাচ্ছ। কিন্তু জবায় অপরাজিতায় বেলপাতায় গন্ধ থাকে নাকি? এ্যাঁ!
—তা তো বটে! পাণ্ডার এতক্ষণে হুঁশ হয়েছিল। গন্ধ তো থাকে না। এলো কোত্থেকে?
–কোত্থেকে? দেখবে? দেখ! নিজের হাতখানা উপরে তুলে ধরে সেদিকে কয়েক মুহূর্ত চেয়েছিলেন, তারপর বলেছিলেন-দেখি তোমার হাত।
তার হাতখানা টেনে নিয়ে নিজের আঙুল ঘষে দিয়ে বলেছিলেন—দেখ! শোঁকো।
পাণ্ডা শুঁকে দেখে বলেছিল—তাই তো।
সেদিন সাধনায় ধ্যানে মগ্ন হয়েছিলেন শ্যামাকান্ত। হঠাৎ মধ্যরাত্রে মনে হল একটি অপূর্ব মধুর গন্ধের বায়ুস্তর তাঁকে আশেপাশে উপর থেকে মেঘের মতই ঢেকে ফেলেছে। তিনি যেন মোহগ্রস্ত হয়ে যাচ্ছিলেন—মনে হল ওই গন্ধের উৎস তাঁর সামনেই রয়েছে, তাঁকে প্রদক্ষিণ করে বেড়াচ্ছে। মনে হল অতি নিকটে। চোখ খুলতে তাঁর সাহস হয়নি। তবে হাত বাড়ালেন তিনি ওই উৎসকে ধরবার জন্য। না, ধরবার কিছু পান নি। কায়াময়ী কেউ ছিল না। তিনি হাতখানা দিয়ে এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত ব্যগ্র আগ্রহে খুঁজলেন। কেউ না। শুধু একটি হিমশীতল স্পর্শ তাঁর আঙুলের ডগাগুলিকে ছুঁয়ে গেল।
চমকে উঠে চোখ খুলেছিলেন তিনি।
শুক্লা চতুর্দশীর জ্যোৎস্নায় অঙ্গন ঝলমল করছিল। নিস্তব্ধতা থমথম করছে। জ্যোৎস্নার মধ্যে কামাখ্যামন্দির ছবির মত মনে হচ্ছিল। কোথাও কেউ নেই। উপরের দিকে চত্বরের ওপাশে তাকালেন। সেখানেও কোন ফুলেভরা গাছ দেখতে পেলেন না। তিনি আবার চোখ বুজে ধ্যানে বসলেন। আবার মনে হল চারিপাশের বায়ুস্তর সেই গন্ধে ভরে উঠেছে।
তুলে নিলেন তিনি জবা এবং অপরাজিতা ফুল অঞ্জলি ভ’রে। জবা এবং অপরাজিতার বর্ণ আছে গন্ধ নেই। বদ্ধাঞ্জলি বুকের কাছে ধরলেন-গন্ধে ভরে গেল নাসারন্ধ্র। তিনি সেই অঞ্জলি ধরেই ধ্যানমগ্ন হলেন। গন্ধের মধ্যেই অবস্থান করেছেন এতক্ষণ পর্যন্ত। তিনি বুঝেছেন, এইবার সামনের দিকে এগিয়ে আসছে আর এক পা ফেলেছে সে। প্রথমে স্বাদে তারপর গন্ধে। সে আসছে? এরপর? শব্দে হয়তো। নুপুর বাজবে? বাজবে কিছু। তারপর বর্ণে-রূপে দেখবেন। তারপর স্পর্শে।
আসবে। সে আসবে। না এসে সে যাবে কোথায়!
মহেশচন্দ্র লিখেছেন—এরপর কামাখ্যায় শ্যামাকান্তের খ্যাতি হ’ল প্রচুর। ভক্ত জুটতে আরম্ভ হ’ল। কিন্তু শ্যামাকান্ত তাতে ভোলেন নি। তিনি হয়ে উঠছিলেন বৈশাখের পিপাসার মত উগ্র শুষ্ক।
ভক্তেরা আশ্রম করে দিলে। কিন্তু সেদিকে তিনি তাকালেন না। দু-চারজন সেবকও জুটল। তারা প্রণামী কুড়োতো। কামাখ্যা মন্দিরে যারা কাজকর্ম করত, তারাই এরা।
শ্যামাকান্ত সে দিকেও তাকাতেন না। তিনি ভাবতেন।
মহেশচন্দ্রই তাঁকে বলেছিলেন—তোমায় লোকে প্রণামী দেয়, সেগুলো ওইসব পাঁচভূতে নিয়ে নেয়। ওগুলো নিয়ে তো তুমি গরীব-দুঃখীদের দিতে পারে!
—তুই দে না।
—আমি তো বিকেলবেলা আসি। লোক তো সারাদিনই আসে তোমার কাছে।
—তা আমি কি করব রে। আমি তো চাইনে। তুই ব্যবস্থা কর। তার চেয়ে এক কাজ কর না!
—কি?
—তুই আমার নায়িকা দেখে দে।
—ও কথা তুমি বলো না আমাকে।
—ওরে বেটা, নায়িকা বললে রাগ করিস। আচ্ছা বিয়ে দিয়ে দে!
—বিয়ে! অবাক হয়ে গেলেন মহেশচন্দ্র। তুমি সন্ন্যাস ছেড়ে বিয়ে করবে?
—কেন রে বেটা, সন্ন্যাস ছাড়ব কেন? সে-ই সন্ন্যাসিনী হবে!
—কিন্তু লোকে তা দেবে কেন?
—দেবে রে দেবে! দেবে না! দেখ আজ দুপুরে সে মেয়ে এসেছিল।
—এসেছিল?
—হ্যাঁ বেটা। যে পাঠাবার সেই পাঠিয়েছিল। সেই মাগী। পাঠিয়েছিল। কুলীন বামুনের ষোল বছরের আইবুড়ো মেয়ে; বাপ নেই; কামাখ্যা দর্শন করে আমার কাছে এসেছিল। আমি তাকে দেখেই বুঝেছি। এ মেয়েকে সে-ই পাঠিয়েছে। মেয়ের মা বললে—বাবা আশীর্বাদ কর যেন বর মেলে। আমরা কুলীন বামুন তার উপর বাপ নেই, এই বিদেশে পড়ে আছি, মেয়ের বিয়ে দিতে পারি নি—তুমি আশীর্বাদ কর। এ সেই মেয়ে রে। কাল তাদের আসতে বলেছি। আসবে। তুই আসিস।
পরের দিন মহেশচন্দ্র এসে বসেছিলেন। তখন ওই আশ্রমে বসছেন শ্যামাকান্ত। সকাল থেকে যারাই এসেছে তাঁকে দর্শন করতে শ্যামাকান্ত তাদের বলেছেন—আজ না। আজ না। যাও, আজ যাও। কণ্ঠস্বরে অধীরতা; ঘাড় নাড়া, হাত নাড়া সবের মধ্যেই একটা অধীরতা। মহেশচন্দ্রের চিত্ত কিছুটা বিরূপ হয়ে ছিল। তিনি শ্যামাকান্তকে শ্রদ্ধা করলেও ভয় করতেন না। তিনি বলেছিলেন—এত অধীর হয়ে পড়েছ তুমি একটা মেয়ের জন্যে। এই তোমার সাধনা?
শ্যামাকান্ত বলেছিলেন—তুই মূর্খ রে, তুই মূর্খ
—আমি মূর্খ? আর তুমি এই সাধক?
—হ্যাঁরে, আমি সাধক। এ সাধনার কি বুঝিস রে বেটা?
—বুঝে আমার কাজ নেই। নারী নিয়ে সাধনা—
বাধা দিয়ে শ্যামাকান্ত বলেছিলেন—বেটা, সংসারে সৃষ্টির সাধনাটা কি বল তো? ওরে বেটা, পুরুষ আর প্রকৃতি, শিব আর শক্তি এদের খেলাতেই সৃষ্টি। ওরে বেটা, সে শক্তির জন্যে শিব তপস্যা করে নি?
—করেছিল। কিন্তু মদনভস্ম জান না?
—সেই তো রে। ভস্ম করে আবার বাঁচাতে হয়। ও মরে না। থাম, থাম। আসছে।
চারিদিক তাকিয়ে দেখেছিলেন মহেশচন্দ্র। দেখতে পেয়েছিলেন অনেকটা নীচে একদল যাত্রী আসছে। কিন্তু মানুষ ঠিক চেনা যায় না। তিনি প্রশ্ন করেছিলেন—চিনতে পারছ তুমি এখান থেকে?
—মন বলছে। মন বলছে! দেখ, পরখ কর! স্থির ব্যগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন তিনি পথের দিকে। কামাখ্যা পাহাড়ের আঁকা-বাঁকা পথ। দুধারে তখন ঘন গাছের জঙ্গল। সেকালে এখানে-ওখানে হিংস্র জন্তু থাকত। বাঘও থাকত ওৎ পেতে। লোকজন মিলে কোলাহল করতে করতে আসত। মধ্যে মধ্যে বাঁকে গাছের ফাঁক দিয়ে দেখা যেত যাত্রী আসছে। মুখ দেখা যেত না, চেনা যেত না, শুধু দেখা যেত মানুষদের কারও একটা পাশ, কারও বা কাপড়, এই মাত্র। তারই দিকে তাকিয়ে ছিলেন শ্যামাকান্ত। আশ্রমের সামনে যেখানে রাস্তাটা এসে সামনে পড়েছে, সেখানে যাত্রীর দল উপস্থিত হতেই শ্যামকান্ত বললেন—ওই!
মহেশচন্দ্র দেখলেন, সত্য। শ্যামাকান্তের ষোড়শী কুমারী ইন্সিতাকে দেখে চিনতে দেরী হল না তাঁর।
সেকালে ষোল বছরের মেয়ে সচরাচর কুমারী থাকত না। তখন গৌরীদানের কাল চলছে। গৌরীদানে অক্ষয়পুণ্য। অবিবাহিতা থাকে কিছু মেয়ে, তারা ব্রাহ্মণের ঘরের কুমারী মেয়ে। পাল্টি কুলীনের ঘরের পাত্র তখন দুর্লভ। এক-একটি কুলীনের ছেলে দশ-বিশ-পঁচিশ-পঞ্চাশ পর্যন্ত বিয়ে করে। বিষ্টুঠাকুরের সন্তান তারাচরণের নাম জানতেন মহেশচন্দ্র, লোকে বলত যেটেরা তারাচরণ। বিশ-পঁচিশ বছরের কুলীনের মেয়ের বিয়ে হত ষাট বছরের বৃদ্ধের সঙ্গে। গঙ্গাযাত্রার পথে বিয়ে করে কুলীনের ঘরের ত্রিশ বছরের মেয়ের সিঁথিতে সিঁদুর দিয়ে অক্ষয়পুণ্য করে যান তাঁরা—একথা মহেশচন্দ্র জানেন।
মেয়েটি কুমারী তা দেখেই বুঝেছিলেন। মাথায় কোন অবগুণ্ঠন নেই। পিঠে একপিঠ চুল এলিয়ে পড়ে আছে। আঁচলের খুটটি গলায় চুলকে বেড়ে এপাশে ঝুলছে। হাতে কিছু আছে বলে মনে হচ্ছে, শাঁখা নয়, অন্য কিছু কাঁচের চুড়ি বোধহয়।
কাছে আসতেই মহেশচন্দ্র মেয়েটিকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। শ্যামাঙ্গী মেয়ে, বোধহয় কালো বললেই ঠিক হয়, কিন্তু এমন সুষমা এমন লাবণ্য! আয়ত দুটি চোখে আশ্চর্য কিছু আছে। আয়ত চোখদুটির নীলাভ শুভ্রতার মধ্যে আকাশের উদাস প্রসন্নতা এবং তেমনি মৃদুদীপ্তি তারার স্থিরতা তার কালো তারাদুটিতে। আশ্চর্য শান্ত! মন স্নেহে কারুণ্যে ভরে উঠেছিল মহেশচন্দ্রের।
সঙ্গে একটি প্রৌঢ়া বিধবা ছিলেন।
যাত্রীর দল উঠে চলে গেল একটু উপরে মন্দিরের দিকে, প্রৌঢ়া বিধবা কুমারীটিকে নিয়ে শ্যামাকান্তের আশ্রমে ঢুকলেন। শ্যামাকান্তকে প্রণাম করে তাঁর সামনে বসে বললেন-আজ আমাকে আসতে বলেছিলেন।
শ্যামাকান্ত ওই কন্যাটির দিকে বিচিত্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন। মেয়েটি লজ্জায় মুখ নত করে মাটির দিকে তাকিয়ে রইল। শ্যামাকান্ত বললেন—মুখ তোল, তোমার কপাল দেখি!
মেয়েটি মুখ তুললে কোন রকমে।
—হুঁ।
প্রৌঢ়া বললে–বিয়ের যোগ আছে কিনা দেখুন বাবা। আমার বোনঝিও বটে সতীনঝিও বটে। বাপ-মা দুই গিয়েছে। পাঁচ বছর যেতে না যেতে খেয়ে বসে আছে। উঁচু কুলীনবংশ। তার ওপর মেয়ের অষ্টমে মঙ্গল। গণকে বলে—মেয়ের হাতে সন্ন্যাসযোগ আছে। মেয়ের সন্ন্যাস-যোগ মানে বিয়ে হবে না। আমি তো চিরজীবী নই। মরব তো একদিন। তখন কি হবে? বিধবা হয়ে থাকে, সে এক কথা, গতর আছে খেটে খাবে। তাই বা পাল্টা ঘর নইলে যার-তার হাতে ওর সাতপুরুষকে নরকস্থ করে দিই কি করে! পয়সা নেই, টাকা নেই যে, যশোর-খুলনাতে ওদের পাল্টা ঘর আছে, সেখান থেকে লোক পাঠিয়ে একটা বুড়ো ধাড়া ধরে আনব। তারপর যা আছে কপালে তাই হবে। সে সন্নোসিনী হোক, আর যা হবে হোক, আমি দেখতে আসব না।
—দেখি, তোমার হাত দেখি।
মেয়েটির হাত দেখে শ্যামাকান্ত বলেছিলেন—হুঁ। সব লক্ষণ আছে! সব।
—সে কি বাবা?
—ঘর ওর নেই। সন্ন্যেসিনী হতে হবে ওকে।
—তাহলে? তুমি একটা কবচ-টবচ দাও না বাবা!
—দেখ, আমি ফুলে মেল, ভরদ্বাজ গোত্র। বিষ্টঠাকুরের সন্তান নৈকুষ্যি। তোমাদের কি? তবে আমি তো সন্ন্যোসী, আমার ওসব এখন নাই। তোমাদের কি?
—কি বলছ বাবা?
—কোন মেল, কার সন্তান, কি রকম ঘর তোমাদের পাল্টা?
—আমরা বাবা, তোমাদের পাল্টাই বটে। ফুলে মেল কেশব চক্রবর্তীর সন্তান, নৈকুষ্যিও বটে। যশোরে বাড়ী ছিল; পেটের দায়ে ধুবড়ীতে এসেছিল ওর বুড়ো বাপ। বুড়ো বয়সে আমাদের দু বোনকে বিয়ে করে ঘাড়ে করে এসেছিল। আমাদের রূপ দেখে ছাড়তে পারে নি। নিজে ছিল কালো কুচ্ছিত।
—হ্যাঁ-হ্যাঁ। বুঝলাম। তা আমার হাতে ওকে দেবে?
—ভৈরবী করবে?
—আগে সাতপাক দিয়ে মন্ত্র পড়ে বিয়ে করব, তারপর আমি যখন ভৈরব তখন ও ভৈরবী হবে। শিব বিয়ে করে নি?
—তুমি যে সন্ন্যোসী হয়েছ বাবা, তা আবার বিয়ে কি করে করবে?
—বললাম তো। শিব বেটা তো যোগী সন্ন্যাসী। তপস্যা করছিল। সে কি করে বিয়ে করলে রে? অ্যাঁ? শাস্ত্র? শাস্ত্রে যা চাইবি তাই পাবি!
অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল প্রৌঢ়া তার দিকে। মেয়েটিও পলকহীন দৃষ্টিতে শ্যামাকান্তকে দেখছিল।
শ্যামাকান্ত বলেছিলেন—এই দেখ, আমার আশ্রম। সিদ্ধি আমার হয়েছে। তবে পূর্ণ সিদ্ধি হয় নি। বুঝলি? তা সস্ত্রীক তপস্যাতে বসলেই সিদ্ধি হবে। তোর মেয়ের কপালে সন্ন্যোসিনী যোগ আছে, সিদ্ধি ওরও হবে। বুঝলি? সাক্ষাৎ শক্তি। হ্যাঁ। তখন ঘর চাইলে রাজবাড়ী হবে। কুবের এসে ভাণ্ডারী হবে। তা ও গয়নাগাঁটি পরবে না। না—তা পরতে চাইবে না। কি কনো? তোর কি মন? এ্যাঁ? আমি শিব হব। শিবের মতন বর চায় মেয়েতে। অ্যাঁ?
একটু, এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলেছিলেন—তবে আমি শিবের মত বুড়ো নই। বয়স তিরিশ পার হয় নি! বলে হা-হা করে হেসেছিলেন।
প্রৌঢ়া বলেছিল-তা বিয়ে করে ফেলে দিয়ে বোম বোম করে চলে যাবে না তো বাবা?
হা-হা শব্দে হেসে কামাখ্যা পাহাড়টাকেই চকিত করে তুলে শ্যামাকান্ত বলেছিলেন—না- না-না। তোর মেয়ে মরলে তাকে কাঁধে ফেলে সতী-সতী করে ঘুরে বেড়াব তিন ভুবন। কি নাম তোর মেয়ের?
—শিবানী।
—আচ্ছা, আচ্ছা। শিবানী-শিবানী করে বুক বাজিয়ে ঘুরব। ক্ষেপে যাব। ফেলে আমি যাব না। বুঝলি! ও আমার জন্ম-জন্মের শক্তি রে। ওকে দেখেই চিনেছি। আর আমি মরব না, আমি মরব না, বিধবা ও হবে না। জন্ম-জন্ম ও সধবাতেই মরেছে। বুঝলি?
মহেশচন্দ্রও শুনে বিস্মিত হয়ে তাকিয়েছিলেন তার দিকে।
প্রৌঢ়া পরের দিন মহেশচন্দ্রের বাড়ী এসেছিলেন অনেক খুঁজে খুঁজে। বলেছিলেন—বাবা, তোমার কাছে এলাম। শুনেছি, তোমার সঙ্গে পাগলাবাবার খুব খাতির! আমার শিবানী রাজী হয়েছে বাবা। বলেছে—মা-মাসী, শিবানী আমাকে মা-মাসী বলে, বললে—আমাকে ওঁরই হাতে দাও মা-মাসী। আর বেশী কি বলবে বল? তা আমার মনে খুঁতখুঁত একটু আছে, সেটি ওঁকে আমি বলতে পারছি না। তোমাকে বলতে এসেছি।
—বল কি বলছ?
—বলছি বাবা, শিবানীকে আমি ওঁর হাতে দোব, বিয়েতে কিন্তু কিরে করণে খুঁত থাকলে হবে না। আর আমাকে বাবা থাকতে দিতে হবে আশ্রমে। আমি শিবিকে ছেড়ে থাকতেও পারব না। আর, আর বাবা, ওইসব পাঁচজনাতে পেনামী-টেনামী কুড়িয়ে মেরে দেয়, সে সবের ভার আমি নোব। আমার জন্যে তো নয়, ওই ওদের জন্যে। ভেবে দেখ বাবা। আয় আগন বাঁধও তো করতে পারব!
কথাটা মহেশচন্দ্রের মন্দ লাগে নি। এই প্রৌঢ়া যদি মায়ের মত পাগলের সংসার পেতে দিয়ে সংসারী করে তুলতে পারে, তবে সে খুব ভাল হবে। অন্ততঃ ওই মেয়েটি একটা জোর পাবে। তিনি বলেছিলেন—বেশ তো, আমি বলব। তুমি ভেবো না মা, আমি পাগলের মত করাতে পারব।
মত তিনিই করিয়েছিলেন। তবে শ্যামাকান্ত বলেছিলেন—তা পেনামী ও-বেটী কুড়োক। জমা করুক, বুকে চাপিয়ে মরুক, কিন্তু আমার সাধনভজন নিয়ে কিছু বলতে পারবে না। সে সব কথা হবে আমার ওই মেয়ের সঙ্গে।
মহেশচন্দ্র বলেছিলেন—তুমি ওই মেয়েকে মদ খাওয়াবে নাকি?
—মদ কি রে বেটা, মদ কি? সুধা! কারণ! পূর্ণাভিষেক হবে, দীক্ষা হবে, ভৈরবী হবে, কারণ না করলে হবে কেন?
—নাঃ, এ তুমি করো না। একটি এমন মেয়েকে বিয়ে করছ, তাকে নিয়ে ঘর-সংসার কর, সুখী হও। তুমি তো সাধন করে পেয়েছ কিছু। আবার কেন?
হা-হা করে হেসে শ্যামাকান্ত বলেছিলেন—দুর শালা, কিছুতে কি হবে রে? কিছুতে? কিছুও যা, ফক্কাও তাই। আমি কি কানা কুকুর, মাড় চেটে পেট ভরাব? শোন-শোন-শোন। গান শোন! গান এসেছে—
মন করিস নে, ছিঁচকে চুরি
পারিস যদি কর ডাকাতি
আন লুটে রাজার পুরী।
নয় গেরস্ত, নয় জমিদার,
লুঠে আন রে রাজার ভাঁড়ার—
টেক্কা নিয়ে কর রে কাবার
সাহেব বিবি নওলা দুরি।
টেক্কা দিয়ে তুরূপ মেরে
শিব পেয়েছে শক্তিকে রে
শিবের টেক্কা নে রে কেড়ে
তবেই বুঝি বাহাদুরি—
মন করিস নে ছিঁচকে চুরি।
এখানে নাই পাপপুণ্য (হেথা)
শূন্য পূর্ণ পূর্ণ শূন্য
শূন্য পূর্ণ ধন্য করে
নাচা রে এক কালো নারী।
সুরেশ্বর বললে—মহেশচন্দ্রের চিঠিতে তিনি গানটিও উদ্ধৃত করেছেন সুলতা। লিখেছেন -গানখানি আমার বড়ই ভাল লাগিয়াছিল, খাতায় লিখিয়া রাখিয়াছিলাম। তাহাও পত্রে লিখিলাম। এবং সেদিন মনে মনে বুঝিয়াছিলাম, এতাদৃশ ব্যক্তিকে সাংসারিক বুদ্ধি লইয়া বিচার করিয়া বড়ই অন্যায় করিয়াছি। সেদিন শ্যামাকান্ত যে চারজনের কথা বলিয়াছিলেন, তাহাও বিশ্বাস হইয়াছিল। এবং সেই দিন দৃঢ়বিশ্বাস হইয়াছিল এই কুমারীকেই স্বয়ং ভগবতী তাঁহার সাধনার জন্যই পাঠাইয়াছেন। নারী লইয়া তান্ত্রিকেরা সাধনা করেন, তাঁহারা সে সব শক্তি নানানভাবে জাতি-বিচার আচার-বিচার না করিয়াই করেন। শ্যামাকান্তের ভাগ্য প্রসন্ন, ভগবতী তাঁহার ধর্মপত্নীসহ সাধনা তপস্যার ব্যবস্থা করিবার অভিপ্রায়েই এমত ব্যবস্থা করিয়াছেন। এবং আমি উদ্যোগী হইয়াই এ বিবাহের ব্যবস্থা করিলাম। আমারই গৃহে কন্যা সম্প্রদান করিলেন শিবানী দেবীর বিমাতা ও মাসীমাতা। রাত্রে বিবাহ শেষ হইল, পরদিনই শ্যামাকান্ত শিবানী দেবীকে দীক্ষা দেওয়াইলেন, তাঁহার বিমাতাকে দিয়া। যাগযজ্ঞ যাহা করিবার নিজে শ্যামাকান্ত করিলেন, বীজমন্ত্র বলিয়া দিলেন, তাহা লইয়া শিবানী দেবীর বিমাতা প্রদান করিলেন শিবানী দেবীর কর্ণকুহরে।
যজ্ঞ শেষ করিয়া শ্যামাকান্ত উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন, শিবানী দেবীকে বলিলেন—তোমাকে আমি এইবার পুরশ্চরণ ও পূর্ণাভিষিক্ত করিয়া সন্ন্যাস দিব। তুমি মনে করিবে, তুমি সাক্ষাৎ শক্তি। এবং আমি স্বামী সাধক সন্ন্যাসী, আমি শিব। হ্যাঁ। কিছুদিনেই তুমি নিশ্চয় বুঝিতে পারিবে যে, শক্তি তোমার মধ্যে আসিয়াছেন।
বধূবেশিনী শিবানী সেদিনও বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকাইয়া বসিয়াছিল। আমার আজও স্মরণ রহিয়াছে—শ্যামাকান্ত হঠাৎ কালী কালী বলিয়া উঠিয়া চলিয়া গেলেন, তাঁহার জপের আসনে বসিবার সময় হইয়াছিল; আমরা তিনজন বসিয়া ছিলাম; শিবানী দেবী, তাঁহার বিমাতা এবং আমি। শিবানী দেবীর বিমাতা শিবানীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—শিবি, তোর কি ভয় করিতেছে? শিবানী দেবী বলিয়াছিলেন—কিছু বুঝিতে পারিতেছি না মা-মাসী! সে অত্যন্ত অসহায় ভাব! শিবানী দেবীর বিমাতাই তাঁহাকে সাহস প্রদান করিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন—ভয় কি? তুই এমন বাপের কন্যা। তোর বাপও তান্ত্রিক ছিলেন, তবে গৃহী। আমরা দুই ভগ্নী তাঁহার মন্ত্রে দীক্ষা লইয়াছিলাম, পূর্ণাভিষিক্ত হইয়াছি। পুরশ্চরণ করিয়াছি। কোন প্রকার ভয় নাই। সাহস অবলম্বন কর। এত বড় সিদ্ধ সাধকের সহধর্মিণী হইলে, তোমার মত ভাগ্য আর কাহার হয়; এই জন্মেই তোর মুক্তি হইবে। দেখিস মা, সিদ্ধি হইলে আমার তোর পিতামাতার যাহাতে মুক্তি হয়, জন্মান্তর চক্রপাক ছিন্ন হয়, তাহাই যেন করিস! আর আমি তো রহিলাম, ভয় কি?
মহেশচন্দ্র লিখেছেন —“আমি নিজেও সেদিন এই মেয়েটিকে সাহস দিয়াছিলাম; বলিয়া- ছিলাম—আমিও রহিয়াছি। উনি আমাকে ভালবাসিয়া থাকেন। এবং আমি অনেক কথাই উহাকে সাহস করিয়া বলিয়া থাকি, উনিও তাহাতে কর্ণপাত করেন, বিবেচনা করেন। আমি সর্বদাই লক্ষ্য রাখিব। তোমার কর্ম হইবে মানুষটিকে শান্ত করা, তুষ্ট করা। তাহাতে উনিও শান্ত সুখী হইবেন, তুমি শান্তি সুখ পাইবে। এ তো অপর কিছু নহে, ধর্মপথে জীবনযাপন। সেই সংসারে উত্তম পথ, শ্রেষ্ঠ পথ, সুতরাং ভয়ের কি রহিয়াছে?”
শিবানী দেবীর বিমাতা বলিয়াছিলেন বাবা, মা কামাখ্যার সম্মুখে এই কথা তুমি বলিলে, আজ হইতে তুমি শিবানীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হইলে। ও তোমার ভগিনী হইল। কেমন?
আমি বলিলাম- তাহাই হইল!
শিবানী ইহাতে যেন আশ্বস্ত হইয়াছিল।
শ্যামাকান্তকেও এই কথা বলিয়াছিলাম। তিনি উৎফুল্ল হইয়া বলিয়াছিলেন—ভালই হইল রে। তুই আমার শ্যালক হইলি। তোকে শালা বলিয়া গাল দিব। তোর ইংরিজীয়ানাকে ভয় করিতে হইবে না। বলিয়া হা-হা করিয়া হাসিয়াছিলেন।
এর পর নাকি কিছুদিন শ্যামাকান্ত আশ্চর্যভাবে সুন্দর স্বাভাবিক মানুষ হয়ে উঠেছিলেন। সেই অশান্ত, অধীর, চঞ্চলতা তাঁর ছিল না। জীবনের ওপর মায়া-মমতা হলে মানুষ নিজের চারিদিকটা যেমন সুন্দর করে গড়ে তোলে, তেমনি করে গড়ে তুলেছিলেন, আশ্রমে একখানি ঘর ছিল, তার সঙ্গে আর দুখানি ঘর করিয়েছিলেন। সামনে কিছু ফুলগাছ লাগিয়ে একটি বাগান তাও করেছিলেন। দেহে শ্রী এসেছিল। পূজাঅর্চনায় কিন্তু অবহেলা, শৈথিল্য আসে নি। সে নিয়মমত করে যেতেন। ভক্ত যারা আসত, সেকালে কামাখ্যা দুর্গম তীর্থ ছিল, তান্ত্রিক সন্ন্যাসী এবং কিছু কিছু দুঃসাহসী যাত্রী আসত। তাদেরও অধিকাংশ ময়মনসিং, ধুবড়ী, কুচবিহার অঞ্চলের যাত্রী। এরা এলে এদের কথা শুনতেন, তাদের কাছে প্রণামী নিতেন। শিবানীকে বাঁ পাশে নিয়ে বসে থাকতেন, দেখে সত্যই যেন শিব ও সতীর মত দেখাত। শ্যামাকান্তের দেহ নধর হয়ে উঠেছিল, তাঁর গৌরবর্ণ উজ্জ্বলতর মনে হত। বড় বড় চোখ, নেশায় রক্তাভ এবং ঢুলটুল করত। কপালে গোল সিঁদুরের টিপ, গলায় মোটা রুদ্রাক্ষ। শিবানীর যখন বিবাহ হয়, তখন ষোড়শী হলেও রোগা ছিলেন, গায়ের রঙ ছিল কালো। কিন্তু তার দেহেও এসেছিল লাবণ্যের জোয়ার। দেহ ভরে উঠেছিল, গায়ের রঙে ফুটেছিল একটি পেলব সুষমা। চুল ছিল প্রচুর। সে চুলে সন্ন্যাসিনী ভৈরবী বলে তেল দিতেন না; রুখু চুল ফুলে ফেঁপে মুখখানিকে ঘিরে এলিয়ে পড়ে থাকত, সামান্য বাতাসে উড়ত। মুখে প্রসন্ন হাসি। পূজাঅর্চনার আয়োজন এবং শ্যামাকান্তের সেবাতেই থাকতেন অহরহ মগ্ন। সন্ধ্যায় শ্যামাকান্ত নিত্য গান রচনা করে গান করতেন।
সময়টা সে-কাল সুলতা। তার উপর কামাখ্যাতীর্থের গণ্ডীর মধ্যে ছিল তাঁদের আশ্রম। লোকে যে মন নিয়ে আসত, তাতে তাঁকে দেখে লোকে বলত—সাক্ষাৎ মা!
দেখিয়া শুনিয়া মনে মনে বড়ই আনন্দলাভ করিয়াছিলাম। মহেশচন্দ্রের পত্রে রয়েছে—শিবানী দেবীর বিমাতা দেহত্যাগ করিলেন। নবম মাসে জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়া কয়েক দিবসের মধ্যেই তদীয় প্ৰাণবায়ু নির্গত হইল। ইহার পরও কিছুদিন শ্যামাকান্ত শান্তই ছিলেন। হঠাৎ কি ঘটিল তিনি জানিতেন, প্রথমেই কেমন যেন স্তম্ভিত স্তব্ধ হইয়া গেলেন। কাহাকেও কিছু বলেন না। চিন্তান্বিত বলিয়া মনে হইত।
আমি জিজ্ঞাসা করিতাম কি হইয়াছে? এত চিন্তা কর কিসের?
তিনি নিরুত্তর থাকিতেন। তাহার সে দৃষ্টি দেখিয়া আমারও ভয় লাগিত।
একদিন বলিলেন—সব ভুল হইয়া গেল। সব।
জিজ্ঞাসা করিলাম—কি?
বলিলেন—তুই বুঝিতে পারিবি না।
ইতিমধ্যে কয়েকজন যাত্রী আসিয়াছিল তাহাদিগকে কুৎসিত গালিগালাজ দিয়া বলিলেন- যাও—যাও—যাও। এখানে কিছু নাই। এখানে কিছু নাই। ফাঁকি। ফাঁকি।
সে চীৎকার বীভৎস চীৎকার। হঠাৎ আবার থামিয়া গালিগালাজ শুরু করিলেন কোন নারীকেই। যেমন পূর্বে করিতেন।
আমি বাধা দিতে চেষ্টা করিলাম পূর্বের মত, কিন্তু সেদিন ক্ষিপ্তের মত উঠিয়া আমাকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। আমি অপমানিত বোধ করিয়া উঠিয়া চলিয়া আসিলাম। উঠিয়া চলিয়া আসিতেছি এমন সময় শিবানী দেবী আমাকে মিনতি করিয়া ডাকিলেন—দাদা! আমি তাঁহার আহ্বান উপেক্ষা করি নাই, দাঁড়াইয়াছিলাম, ভাবিয়াছিলাম বলিব—তুমি দুঃখ করিয়ো না ভগ্নী; তোমার উপর কোন রাগ অভিমান করিয়া যাইতেছি না। কিন্তু তাহা বলা হইল না, তাহার পূর্বেই শ্যামাকান্ত গর্জন করিয়া পত্নীর চুলের মুঠায় ধরিয়া তাহার গণ্ডদেশে চপেটাঘাত করিয়া বলিলেন—যা—যা—তুই সুদ্ধ চলিয়া যা। বাহির হইয়া যা!
ইহার পর আমি আর দণ্ডায়মান থাকি নাই, চলিয়া আসিয়াছিলাম। আর কিছুদিন ওদিকে যাই নাই। হঠাৎ একদিন সংবাদ পাইলাম, পাণ্ডারাই সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন যে শ্যামাকান্তের আশ্রমে একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। শিবানী দেবী প্রায় অর্ধমৃত এবং শ্যামাকান্ত কোথায় চলিয়া গিয়াছেন!
তাড়াতাড়ি গিয়া যাহা দেখিলাম, যাহা শুনিলাম, তাহাতে স্তম্ভিত হইয়া গেলাম এবং শ্যামাকান্তকে নরপিশাচ না ভাবিয়া পারিলাম না!
পাণ্ডারা বলিলেন—শ্যামাকান্ত সেই হইতেই আবার উন্মত্ত দুর্দান্তপনা শুরু করিয়াছিলেন। কয়েকদিন কখনও বুক চাপড়াইতেন, চীৎকার করিতেন। এবং চারিদিকে পাগলবৎ ঘুরিতেন। আর নিষ্ঠুর নির্যাতন করিতেন স্ত্রীকে। অকথ্য গালিগালাজ এবং মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে প্রহারও করিতেন।
কয়েকদিন পর একটা পরিবর্তন হইল। শ্যামাকান্ত আরও ভয়ঙ্কর হইলেন। বুক চাপড়াইয়া হায় হায় করিতেন না। গর্জন করিতেন। সবই কামাখ্যাদেবীর প্রতি। ঘটনার দিন সকাল হইতেই ওঁয়া ওঁয়া শব্দ করিতে শুরু করিয়াছিলেন। মন্দিরের সামনে দাঁড়াইয়া ওইপ্রকার শব্দ করিতে করিতে নিজের গলা টিপিয়া ধরিতেছিলেন। আশ্রমে যান নাই। কিছু আহার করেন নাই। হঠাৎ সন্ধ্যার মুখে আশ্রমে ফিরিয়া উন্মত্তবৎ ভৈরবীদেবীকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে কয়েকজন পাণ্ডা আশ্রমের পাশ দিয়া ফিরিতেছিল, তাহারা তাঁহাকে চাপিয়া ধরে, নহিলে শিবানী দেবীকে হয়তো মারিয়াই ফেলিতেন। কিন্তু উন্মত্ত শ্যামাকান্ত তাহাদিগকেও প্রহার করিতে উদ্যত হইতেই তাহারাও তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছিল। এবং ধরিয়া হস্ত বন্ধন করিয়া আশ্রমের ঘরেই বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। শিবানী দেবী তখন আহত, তাঁহার মাথায় আঘাত লাগিয়া কাটিয়া রক্তপাত হইতেছিল। সর্বাঙ্গ প্রহারে জর্জরিত। চেতনা ছিল না। তখন সকলে পরামর্শ করিয়া তাঁহাকে কোনমতে বহন করিয়া পাণ্ডাদের গৃহে আনিয়া সেবা-শুশ্রূষা করিয়া চেতনা সঞ্চার করিয়াছে। তিনি এখনও খুবই কাতর। এদিকে শ্যামাকান্তের আশ্রম শূন্য। যে ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছিল সে ঘরের দ্বার ভগ্ন; শ্যামাকান্ত রাত্রেই হাতের বন্ধন কোনক্রমে খুলিয়া বদ্ধ দ্বার ভাঙিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন।
আমি কি করিব, আমি শিবানী দেবীকে গৃহে লইয়া আসিলাম। পাণ্ডাদের মধ্যে এক বৃদ্ধ প্রবীণ তান্ত্রিক বলিয়াছিলেন—মনুষ্যটি ভ্রষ্ট হইয়া উন্মাদ হইয়া গিয়াছে। এইরূপই হইয়া থাকে। শিবানী দেবী সুস্থ হইলে তাঁহার নিকট যাহা শুনিলাম, তাহাতে ভয়ে বিস্ময়ে ঘৃণায় অভিভূত হইয়া যাইলাম।
সুরেশ্বর চিঠিখানা মুড়ে রেখে বললে—এরপর চিঠিখানায় যে সব ঘটনার বর্ণনা আছে তা সেকালের ভাষায় হয়তো তোমার মনে হবে অশ্লীল। অশ্রাব্য। মহেশচন্দ্র লিখেছেন- এবার তোমার কাছে যাহা বর্ণনা করিতেছি, তাহা তোমার সম্মুখে আমি বাক্যে প্রকাশ করিতে পারিতাম না। পত্রে লিখিতেও ইচ্ছা হইতেছিল না, কিন্তু মা ভবানী আমাকে বলিল —“সমুদয় সত্য বৃত্তান্ত অকপট ভাবে আপনি বিস্তারিত ভাবে তাঁহাকে জ্ঞাত করুন-নতুবা আমার অপরাধ লাঘব হইবে না।”
তিনি যা লিখেছেন তা তোমাকে আমি এ কালের ভাষায় বলছি। বুঝতে তোমার কষ্ট হবে না।
শ্যামাকান্ত বামাচারী তান্ত্রিক—তিনি গোড়া থেকে পুরুষ হিসেবে মহাশক্তিকে চেয়েছিলেন প্রকৃতিরূপে। তিনি তাঁর স্বামী অর্থাৎ প্রভু হবেন। যোগিনী সাধনের মধ্যে তিনি তাঁকে পেতে চেয়েছিলেন কীর্তিহাটের সিদ্ধাসনে বসে। সেখান থেকে জলে ভেসে যেতে যেতে চরে এসে ঠেকে বেঁচেছিলেন। তারপর এসেছিলেন কামাখ্যায়, সেখানে ওই ষোড়শী শিবানীকে দেখে মুগ্ধ হয়ে তাকে বিবাহ করে সস্ত্রীক সাধনায় পেতে চেয়েছিলেন মহাশক্তিকে।
তিনি শিবানী দেবীকে বলতেন—দেবী আসবেন, সাক্ষাৎকার হলে তাঁকে অধিষ্ঠাতা হতে হবে শিবানীর মধ্যে। আর তিনি নিজে পাবেন শিবত্ব। ফলে তাঁদের হবে অনন্ত জীবন অনন্ত যৌবন, আর তাঁরা হবেন অনন্ত শক্তির অধীশ্বর।
বলতেন আর হাসতেন। মধ্যে মধ্যে একটি গান করতেন—যে গানটি তিনি অন্য কারুর সামনে গাইতেন না।
আর তুই পালাবি কোথা?
উঁকি মেরে মুচকি হেসে
ফাঁকি দিয়ে হেথা হোথা।
মেঘের ফাঁকে বিদ্যুতের মত
উঁকি মেরে মুচকি হেসে—
এবার তোকে ধরেছি নাগাল
হয়েছি তালগাছের মাথা।
আর তুই পালাবি কোথা?
শিবানী দেবী ভীত হতেন। তাঁর অন্তরাত্মা ত্রাসিত হয়ে উঠত। তিনি মিনতি করে বলতেন—না—না। এ গান তুমি গেয়ো না।
হা-হা করে হেসে শ্যামাকান্ত বলতেন—ভয় লাগছে তোর! লাগবে। প্রথম প্রথম ভয় হবে যে। সহজ কথা তো নয়! সূর্যি এসে ঢুকবে পিদিমের মধ্যে। বুঝলি না! তখন তো মাটির পিদিম তার সলতে তার তেল সব ফুস হয়ে যাবে। হাঁ। ওই শিখা তখন জ্যোতি হবে। পিদিমের মত তোর ভয় হবে বইকি! কিন্তু সাহস কর। সাহস কর!
শিবানী দেবী প্রাণপণ চেষ্টা করেও সে সাহস অর্জন করতে পারেন নি। তিনি চোখ বুজে ধ্যান করতে গিয়ে ভয় পেতেন। তিনি মনে মনে বলতেন—না—মা—না। তুই এমন রূপে আসিস নে, মা—এমন রূপে আসিস নে। আমাকে লোপ করে দিসনে। শান্ত মূর্তিতে আয়, ছোট হয়ে আয়—মা বলে আয়। আমি তোকে মা বলে ডাকি। তুই ওকে বাবা বলে ডাক। ওর মনকে ভুলিয়ে দে—গলিয়ে দে!
এমনি ভাবেই চলছিল সাধনা। বিলম্বে অধীর হয়ে উঠছিলেন শ্যামাকান্ত। বলতেন—এ কি হ’ল। নাগালের মধ্যে এসেছে অথচ কি হচ্ছে? যেন ছুঁয়ে ছুঁতে পারি না। আচ্ছা দেখি কতদিন এই চার আঙুল বাইরে থাকিস? তুই না এগিয়ে আসিস আমি এগুব। ধরব তোকে।
সেই এক পা সামনে ফেলেই তিনি আর্তনাদ করে উঠলেন। কি যেন ঢুকল পায়ের তলায়। সে এক নিষ্ঠুর যন্ত্রণাদায়ক বিষকন্টক। ওই বিষকন্টক পেতে রেখেই শ্যামাকান্তের নাগালের চার আঙুল বাইরে থেকে একহাত সামনে এক যবনিকা ধ’রে নিজেকে অদৃশ্য রেখে অনন্ত রহস্যময়ী তাঁকে গন্ধে সুরে স্বাদের আভাসে ইঙ্গিতে আহ্বান ক’রে বলছিলেন–এস –এস–এস। শ্যামাকান্ত এগিয়ে যেতে পা ফেলতেই সেই কাঁটাতে আহত হয়ে আর্তনাদ ক’রে বসে পড়লেন।
হঠাৎ সেদিন প্রকাশ পেল-শিবানী দেবী সন্তানসম্ভবা।
শিবানী দেবীই বলেছিলেন। সাধনায় আমি বসব না। আমি–।
শ্যামাকান্ত যেন বজ্রাহত হয়ে গেলেন। সুরেশ্বর বললে —এখুনি বললাম মহাশক্তি বিষকন্টক পেতে রেখে সামনে ডেকে শ্যামাকান্তকে আহত পঙ্গু করে দিলেন। না। তিনি তালগাছ হ’তে গিয়েছিলেন—তিনি বজ্রাগ্নি হয়ে এসে তাঁর মাথায় পড়ে বললেন—আমাকে ধর। আমি এসেছি!
সত্যসত্যই বজ্রাহতের মত শ্যামাকান্ত ঝলসে গেলেন। এ কি হ’ল? তিনি ঘরে গিয়ে উপুড় হয়ে পড়লেন।
সব গেল! এ সাধনায় সঙ্গিনী আছে। সেখানে জাতিবিচার নেই। প্রকৃতি-পুরুষের সহজ আচরণে বাধা নেই। কিন্তু সন্তান তো নেই! এ সাধনায় বর্তমানকেই অনন্তে প্রসারিত করে, ফুল ফোটে, ফল তো নেই, ভবিষ্যতের বীজ তো বহন করে না! ফল হলেই সব গেল। হয়ে গেল। বর্তমান তো নেই, ফুরিয়ে গেল বর্তমান।
মহেশচন্দ্রের চিঠিতে এ সম্পর্কে সেকালের ব্যাখ্যা আছে।
সেই তান্ত্রিক পাণ্ডা তাঁকে বলেছিলেন–এমনিই হয়। মহাপ্রকৃতি সামনে ওই আবরণটি রেখে এগিয়ে এসে ইশারা দেন ওই সব অলৌকিক শক্তির। গন্ধের ইশারা, স্বাদের ইশারা, সুরের ইশারা। সাধক ঠিক থাকলে তিনি নিজেই আবরণ ফেলে দেখা দেন। মা বলে লুটিয়ে পড়লে করুণাময়ী হয়ে তুলে নেন। আর এ পথে এমনি হয়, এ ভুল হবেই, ভুল হলেই আবরণটি পড়ে যায়। ওপারে কোথায় কি? কিছু নেই, শূন্য অন্ধকার, সেখানে দন্তশূন্য জড়তার শূন্য মুখগহ্বরের মত বীভৎস ভয়ঙ্কর এক হাঁ তাকে গ্রাস করতে আসে।
অমৃতের বদলে মৃত্যু আসে।
শ্যামাকান্তেরও মৃত্যু হল। মৃত্যু হয়েও এখানে নিষ্কৃতি নেই। প্রেত হয়। সাধক শ্যামাকান্ত সেই প্রেত হয়ে উঠেছিলেন।
তিনি চেয়েছিলেন শিবানীর গর্ভের সন্তানের মৃত্যু। কিন্তু শিবানী তাকে রক্ষা করতে চেয়েছিল। সেই সংঘর্ষের সময়েই দৈবক্রমে পাণ্ডারা এসে তাঁকে রক্ষা করেছিল।
প্রেত কোথায় কোন নরকের মুখে ছুটেছিল কেউ খোঁজ করে নি। শিবানী দেবী কিন্তু খোঁজ করেছিলেন। তাঁর অনুরোধে মহেশচন্দ্র তাঁর সন্ধান করেছিলেন। মাস দুয়েক পর সন্ধানও পেয়েছিলেন। তখন শ্যামাকান্তের অবস্থা নরকের প্রেতের মত।
ধুবড়ী থেকেও কয়েক ক্রোশ দূরে ব্রহ্মপুত্রের ধারে একখানা মুসলমান গ্রাম, উন্মাদ শ্যামাকান্ত তাদের মধ্যেই বাস করছেন। তারা তাঁকে ব্রহ্মপুত্রের তটের এক নির্জন শ্মশানে একদিন সকালে একটা অর্ধজ্বলন্ত চিতার ছাই এবং অঙ্গারের উপর উপুড় হয়ে পড়ে থাকতে দেখেছে। দুরে ছিল একটা শব আর একটা অজ্ঞান ব্রাত্যনারী। তারা নৌকার মাঝি। ওই শ্মশানে তখন কিছুদিন শ্যামাকান্ত বাস করছিলেন। তারা তাঁর গন্ধ আনার শক্তির কথা জানত। মাটিকে ছাইকে গুড় করতে পারার ক্ষমতারও পরিচয় পেয়েছিল। সেদিন সকালে সেই গন্ধবাবাকে চিতায় এমন ক’রে পড়ে থাকতে দেখে তারা তাঁকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল নিজেদের গ্রামে। সমস্ত মুখটা পুড়ে গেছে। চেহারা হয়েছে প্রেতের মত। দেহের ক্ষত ভাল হয়েছে কিন্তু ঘোরতর উন্মাদ। ওদের মধ্যেই বাস করছেন। ওদের সঙ্গেই খাচ্ছেন। কোন বিচার নেই।
এ কথা শিবানী দেবীকে মহেশচন্দ্র জানাতে পারেন নি। গোপন রেখেছিলেন কথাটা।
সাত মাস পর শিবানী দেবীর সন্তান হল–কন্যা-সন্তান!
মহেশচন্দ্রর চিঠিটা খুলে সুরেশ্বর আবার পড়ল—এই কন্যাই ভবানী! আমার গৃহেই ভবানী ভূমিষ্ঠা হইয়াছিল।
মদীয় পত্নী সন্তানসন্তুতিহীনা। অতি মমতাময়ী ছিলেন এবং ধর্মপ্রাণাও ছিলেন। তদীয় ধর্মপ্রাণতার জন্যই আমি যৌবনে ক্রীশ্চান ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াও সে ধর্ম গ্রহণ করিতে পারি নাই। তিনি শিবানী দেবীকে সাতিশয় শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন। ভবানী ভূমিষ্ঠ হইবার পর তিনিই একরূপ তাহার মাতা হইয়া তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়াছিলেন। কারণ শিবানী দেবী সন্তান-প্রসবের পর আবার কঠোরভাবে সন্ন্যাসিনীর মতই জীবনযাপন করিতেন। আচার আচরণ, এমন কি তন্ত্রমতে পঞ্চপর্বে উপবাস করিয়া থাকিতেন, সমস্ত রাত্রি বসিয়া থাকিতেন জপের আসনে।
কন্যাকে দেখিতেন মদীয় পত্নী।
তিন বৎসর পর তিনি সজ্ঞানে দেহত্যাগ করেন। সামান্য জ্বর হইয়াছিল। সম্মুখে তিনদিন পর ছিল বৈশাখী পূর্ণিমা। দ্বিতীয় দিন হইতেই আমাকে এবং মদীয় পত্নীকে ডাকিয়া বলিয়া- ছিলেন—আমি আগামীকল্য সম্ভবতঃ দেহরক্ষা করিব। এই কন্যা আপনাদিগকে দিলাম। আপনারা ইহাকে পালন করিবেন। এই কন্যাকে বিবাহ দিবেন না। বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে উহার পিতা-মাতার বৃত্তান্ত সমস্ত বলিয়া বলিবেন যে, তাহার পিতাকে পাপমুক্ত করিবার জন্যই তাহার জন্ম। সে যেন সমস্ত জীবন শুদ্ধাচারে থাকিয়া মহামায়ার পূজা করে। কোন শুদ্ধ সাধুকে জিজ্ঞাসা করিলেই তিনি বিধি বলিয়া দিবেন। হাসিয়া বলিয়াছিলেন—বিবাহই বা কে করিবে! প্রথমতঃ এই সন্ন্যাসের মধ্যে যাহার জন্ম তাহার জাতি নাই। তাহার উপর তিনি জাতি হারাইয়া মুসলমানদের মধ্যে বাস করিতেছেন! কে তাহাকে বিবাহ করিবে? আর বিবাহ দিতে গেলেই তাঁহার পরিচয় জানাজানি হইবে। সে যেন না হয়। আর কোনরূপ অনাচার-যে মদ্যপায়ী, যে পরদারাসক্ত, তাহার সংস্রব-এ কন্যার সহ্য হইবে না। এরূপ হইলে ইহার মৃত্যু হইবে।
তুমি যখন উপযাচক হইয়া বিবাহ করিতে চাহিলে, তখন তোমার মত পাত্র পাইয়া ভবানীর ভাগ্য ভাবিয়াই প্রলোভন সংবরণ করিতে পারি নাই। ভাবিয়াছিলাম সব কথাই তোমাকে বলিব, তুমি জানিয়া যদি বিবাহ কর তবে আপত্তির কি আছে? কিন্তু সব বলিতে পারি নাই। শিবানী দেবীকে স্মরণ হইয়াছিল। শুধু বলিয়াছিলাম—কন্যাটি এক সিদ্ধ তান্ত্রিক সন্ন্যাসীর কন্যা। তাঁহারা সস্ত্রীক সন্ন্যাসী হইয়া তন্ত্র-সাধনা করিতেন। কন্যাটিকে আমাকে দান করিয়াছেন। তাঁহাদের নাম জানিতে চাহিও না। এবং মদ্যপান বা কোনপ্রকার পরনারী সংস্রব করিতে পারিবে না, যদি এরূপ শপথ কর তবে বিবাহ দিতে পারি।
তুমি তাহাতে রাজী হইয়াছিলে!
বীরেশ্বর রায় চিঠিখানা পড়ে চোখ বুজে চুপ করে বসেছিলেন।
সামনে ছেদী সিং এক পায়ের উপরেই ভর দিয়ে উপুড় হয়ে বসেছিল। এতক্ষণ ধরেই সে বসে আছে। একটি বাক্য উচ্চারণ করে নি। শব্দ করে নি। ১৮৫৮ সালের কীর্তিহাটের কাছারি চলছে নিচে।
পাইকদের হাঁকডাক চলছে। নায়েব-গোমস্তার শাসনবাক্য শোনা যাচ্ছে। আস্তাবলে ঘোড়ার ডাক উঠছে।
হাতীটা কোথাও থেকে এল, গজেন্দ্র গমনের তালে তালে শেকলে বাঁধা ঘণ্টা বাজছে ঢঙ-ঢঙ! ঢঙ-ঢঙ!—ঢঙ-ঢঙ!
অনেক লোকের আওয়াজ শোনা গেল। বোধ হয় কোন মহলের প্রজারা এসেছে। বীরেশ্বর রায়ের কাছে এসবের অস্তিত্বও যেন ছিল না। তাঁর মনে এই বিচিত্র কথাগুলিই ঘুরছিল। কালটা সেকাল। অবিশ্বাস তিনি করেন নি। তিনিও তো দেখেছেন এমন মানুষ। কলকাতার ময়দানের ঘাসের বন আর জঙ্গলের মধ্যে এক পাগল হাতে ঘষে গন্ধ দেয়, মাটি তুলে দিলে গুড় মনে হয়। অপরূপ কণ্ঠস্বর তার। স্তব্ধ রাত্রে গান শুনে চোখে জল আসে। মধ্যে মধ্যে গলা টিপে ধরে বলে—ছেড়ে দে-ছেড়ে দে। বলতে দে!