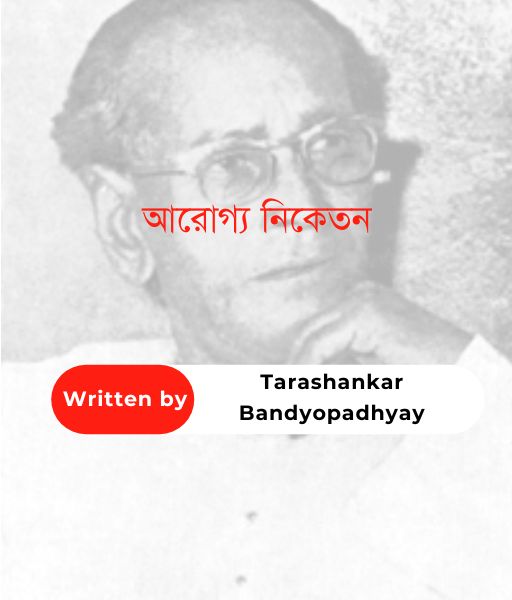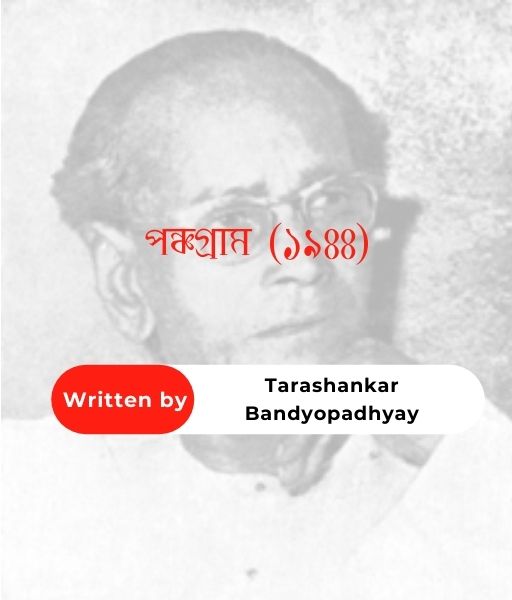প্ৰথম খণ্ড – দ্বিতীয় পর্ব : ২.১
সুরেশ্বর বললে সুলতাকে-আমার যে কি আনন্দ হচ্ছে সুলতা, তোমাকে এই আজকের দিনটিতে পেয়ে সে কি বলব! আজ ১৯৫৩ সালের ২৫শে নভেম্বর হয়তো বা বিধাতাই ধার্য করে রেখেছিলেন যে দীর্ঘ পনেরো বছর পর তোমার সঙ্গে আমার দেখা হতেই হবে!
সুলতা হাসলে। বললে-কেন, বিধাতার কি দায় পড়েছিল। দেখা তো তুমি এর আগে করলেই পারতে। তোমার কোন লজ্জার বালাই আছে বলে তো বিশ্বাস করি নে। তুমি কলকাতায় এসেছ। আমি জানি মাসে একবার তো এসেছই—কোন মাসে দুবারও এসেছ। আমি খোঁজ পেয়ে ফোন করেছি—তুমি ফোন ধরতে না, চাকরে ধরত, তুমি বলতে—বল বাড়ী নেই বাবু। কথাটা ক্ষীণভাবে হলেও ফোনের মারফত শুনেছি। চাকর তোমায় রিসিভারের সাউন্ডপিসে হাত চাপা দিতে জানত না, তুমিও শেখাও নি। তাছাড়া দুবার তুমি আমাকে দেখেও সরে গেছ—মানে গা ঢাকা দিয়েছ। একবার মিউনিসিপ্যাল মার্কেটে, একবার ধর্মতলায়—জি সি লাহার রঙের দোকানের সামনে। বোধহয় রঙ তুলি কিনে বেরুচ্ছিলে। আমি ওপারে মসজিদটার কাছে ট্রামের জন্য দাঁড়িয়ে। তুমি হনহন করে চলে গেলে। কি মিথ্যে বলছি আমি?
সুরেশ্বর বললে—না। মিথ্যে বলনি। সত্য কথা। অস্বীকারই বা আমি করব কেন? আমি আর যাই হই মিথ্যেবাদী নই। মানে যাকে কাপুরুষ মিথ্যেবাদী বলে। নইলে কৌতুক করে অনেক মিথ্যে বলি। রায়বংশের ছেলেরা বেশীর ভাগই সাহসী মিথ্যেবাদী। যেমন ধর, চাকরকে বললাম—বল বাড়ী নেই বাবু অথচ রিসিভারের মুখটা চাপা দিতে বললাম না। ও তথ্যটা আমি জানি না তা তো নয়। জানি। ওটা যাতে তুমি শুনতে পাও—তাই জন্যেই বলেছি এবং বেশ উঁচুগলায় বলেছি, যাতে কথাটা তুমি শুনতে পাও।
—সামনাসামনি বলতে পারতে তো!
—পারতাম না, চক্ষুলজ্জা হত!
—সেটা আজ ঘুচল কেন? আর চোখের লজ্জা তোমার আছে বলেও তো জানতাম না। হেসে সুরেশ্বর বললে—আমিও জানতাম না। কিন্তু তোমার ক্ষেত্রে ওটা যে কেমন করে গজাতো তা আমি নিজেও জানি না!
—সেই তো। আজ সেটা গেল কি করে তাই তো জিজ্ঞেস করছি।
একটু ভেবে সুরেশ্বর সিগারেট ধরালে। তারপর বললে—দেখো—আজকের দিনটা এমন একটা দিন, যে দিনটা পঞ্জিকার অর্ধোদয়যোগে গঙ্গাস্নান বা মেয়েদের অনন্ত ব্রত, সাবিত্রী ব্রত প্রতিষ্ঠা এবং উদ্যাপন করবার দিনের মত। ধর, আমি সংকল্প করেই ব্রত করেছিলাম যে, আজকের দিনটি যতদিন না আসবে, ততদিন আমি জগতে সমাজে নিতান্তভাবে নগণ্য এবং জঘন্যের মত থাকব। আজ সেই দিনটি এল। পঞ্জিকার নয়—ইতিহাসের। ১৯৫৩ সাল ২৫শে নভেম্বর; লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলীতে ব্রতকথা শুনে এলাম। বেরিয়ে আসছি, তোমার সঙ্গে দেখা হল। বুঝলাম, আমার ব্রত ঠিক পালন করা হয়েছে। তোমাকে এবার বললেই আমার ব্রতের সমাপ্তি।
—হুঁ। সুলতা বুঝলে এবার; জমিদারী প্রথা রদ করে বিল পাশ হয়েছে, এবং সুরেশ্বর তাতে আজ ক্ষুব্ধ এবং মর্মাহত হয়ে নির্লজ্জ উদ্ভ্রান্তের মতো কথা বলতে শুরু করেছে। ক্ষোভে হৃদয়াবেগের বাঁধ ভেঙেছে।
ছবিগুলোর দিকে তাকালে সে। সারি-সারি বর্ণাঢ্য ছবি। বিচিত্র বিভিন্ন পদ্ধতিতে আঁকা। প্রথম ছবিখানা যেন সেই কোম্পানির আমলে কোন ইংরেজ চিত্রকরের আঁকা স্কেচের ঢঙে আঁকা ছবি। তবে কালো সাদা রেখাতে নয়—রঙ–তেলরঙে আঁকা। তারপরের ছবিখানা একটি মন্দিরের মধ্যে কালীমূর্তি। মনে হচ্ছে পুরনো আমলের দেশী চিত্রকরের আঁকা ছবি।
লম্বা একটা বারান্দা-ঘেরা ঘর—দৈর্ঘ্যে বোধ হয় একশো পঁচিশ ফুটের কম নয়। ছবিও কম নয়। দু’ সারিতে একটু উঁচু-নিচু করে অনেক ছবির সংকুলান হয়েছে। অন্তত একশোর কম নয়। তা ছাড়াও বারান্দায় দুটো প্রান্তের দুটো দেওয়াল আছে। তাতেও কুড়ি পঁচিশখানা করে চল্লিশ পঞ্চাশখানা।
সুরেশ্বর বলেছে—এটা সে ছবি দিয়ে ‘কীর্তিহাটের কড়চা’ তৈরী করেছে। অর্থাৎ তাদের কীর্তিহাটের রায়বংশের ইতিহাস!
খুব গৌরবোজ্জ্বল ঘটনাগুলিকে এঁকেছে।
একটু হাসি ফুটে উঠল সুলতার মুখে।
১৯৫৩ সালের ২৫শে নভেম্বর, আজ বাংলার বিধানসভার জমিদারী প্রথা রহিত করে বিল পাশ হল। সুলতা অ্যাসেম্বলীর নিচের তলায় দেওয়ালের ধারে যে সরু একটা ফালিতে কিছু দর্শকদের বসবার জায়গা আছে-সেখানেই বসে ছিল। উপর-নিচে সমস্ত গ্যালারী দর্শকে পূর্ণ ছিল। উপরে গভর্নরের গ্যালারীতে ক’জন রাজা-জমিদার বসে ছিলেন, যাঁদের সুলতা চিনত। বর্ধমানের মহারাজার টুপিটা সে খুঁজেছিল কিন্তু নজরে পড়েনি। ওই টুপিটা চেনার কথা তার মনে অক্ষয় হয়ে আছে। এই অ্যাসেম্বলী হাউসের বাগানেই একটা বড় টি-পার্টি হয়েছিল। তাতে এসেছিলেন ইয়োরোপের এক বড় রাজনীতিবিদ। তাঁকে সম্বর্ধনা দেওয়া হচ্ছিল। সম্বর্ধনা শেষে যখন সে বেরিয়ে আসছিল তখন ঘটনাচক্রে সামনেই আসছিলেন প্রাক্তন রাজনৈতিক কর্মী এবং ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত মন্ত্রী ভূপতি মজুমদার মশায়। তিনি তাকে দেখে বলেছিলেন—আরে সুলতা!
সে বলেছিল—ভাল আছেন? প্রণাম করতে গিয়েছিল। কিন্তু ভূপতিদা বলেছিলেন—না-না- না। অ্যাসেম্বলী হাউসের সীমানা গণতন্ত্রের কাশীক্ষেত্র, এখানে প্রণাম নিষিদ্ধ। সে বাবাকেও প্রণাম করতে নেই ছেলের। অ্যাডাল্ট ফ্র্যাঞ্চাইজের বিধানে ভোটাধিকার এখানে আঠারো বছর হলেই আপনি পায়। ইনহেরিটেন্স নেই এবং বাপের বিরুদ্ধে ছেলের ইলেকশনে দাঁড়াতে নিষেধ নেই। প্রণাম এখানে অচল। অধম এখানে কেউ নেই।
বলতে বলতেই থমকে দাঁড়িয়েছিলেন। পার্টির আসরের একেবারে একপ্রান্তে একাত্তে একখানি লম্বা আসনে একটি দম্পতি বসে ছিলেন। স্বামীর মাথায় ছিল একটি টুপি, গড়নটা বিচিত্রও বটে চেনাও বটে। যেন ছবিতে সে দেখেছে। অনেকবার দেখেছে। পরনে শেরওয়ানী চুস্ত পাজামা। কিন্তু কে ঠিক ঠাওর করতে পারেনি। ভূপতিদা থমকে দাঁড়িয়ে হেসে বলেছিলেন—হ্যালো বার্ডওয়ান!
তখন তার মনে হয়েছিল, হ্যাঁ, বর্ধমানের মহারাজার টুপিই তো বটে!
এ মহারাজাকে সে দেখেনি কিন্তু মহারাজ বিজয়চাঁদকে সে দেখেছে। ইউনিভারসিটির কনভোকেশনে দেখেছে। এবং সেকালে তাঁর এই টুপি মাথায় ছবি অনেকবার কাগজে ছাপা হয়েছে মনে পড়ছে তার।
ভূপতিদা বলেছিলেন—আপনি এখানে একপাশে?
মহারাজ বর্ধমান হেসেছিলেন। সে হাসির অর্থ স্পষ্ট।
থাক সে কথা। আজও সেই টুপি সে খুঁজেছিল ওইখানে জমিদারদের মধ্যে। পায়নি। পেয়েছিল পাইকপাড়ার বা কান্দীর কুমার বিমলচন্দ্র সিংহকে। তিনি সেবার ইলেকশনে হেরেছিলেন। আগের বারে তিনিও মন্ত্রী ছিলেন ভূপতিবাবুর সঙ্গে। তিনি বসেছিলেন স্পীকারস গ্যালারীতে, একেবারে প্রথমেই। তিনি অতি সুপরিচিত ব্যক্তি—কি রাজনৈতিক মহলে কি পণ্ডিত সাহিত্যিক রসিক মহলে। চেহারাতেও এমন বৈশিষ্ট্য আছে যে একবার দেখলেই চেনা হয়ে যায়।
আরও একজনকে সে খুঁজেছিল। খুঁজেছিল কাশিমবাজারের মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর উত্তরাধিকারীকে। হ্যাঁ, ওই একজন সন্ন্যাসী জমিদার। প্রাতঃস্মরণীয়। তাঁকে যেন দেখেছিল। মহারাজ শ্রীশচন্দ্র নন্দী। তিনি ছিলেন উপরে। জমিদার কজনের মধ্যে।
সুরেশ্বরকে ঠিক তার মনেই পড়েনি। তাকে খোঁজেওনি। সে এখানে উপস্থিত থাকবার সম্ভাবনার কথা তার মনের মধ্যে উঁকিই মারেনি। সুরেশ্বরকে সে মনের দিক থেকেও মুছেই ফেলেছে। হ্যাঁ, মুছেই ফেলেছে। যখন সুরেশ্বর ওখানে গেল, তখন প্রথম প্রথম বেশ সকৌতুকে ওখানকার সব কিছুকে ব্যঙ্গ করে চিঠি লিখত। লিখেছিল, মনে আছে, এখানকার সেটেলমেন্ট হাকিম হরেন্দ্রনাথ ঘোষ আমারই বয়সী। একেবারে নতুন হাকিম। সুপুরুষ চেহারা। চোখে চশমা আছে, চশমার পাওয়ার শুধু দুর্বল দৃষ্টিকে সবল করেনি, দিব্যদৃষ্টি দিয়েছে। সাপের পাঁচটা করে পা আছে তা তিনি দেখতে পান। সারাদিন দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন ক্যাম্পের আদালতের মাঠে। সেটা ইচ্ছেপূর্বক তা গোপন করেননি ভদ্রলোক। আমার কেস নম্বরটা উঠলেও সেটাকে ঠেলে সরিয়ে রেখেছিলেন। তখনও পর্যন্ত মনে হচ্ছিল তিনি সাপের তিনটে পা দেখেছেন। বেলা বারোটার সময় (আমি গিয়েছিলাম বেলা দশটায়) দেখলাম এক প্রবীণ প্রৌঢ় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে সত্যিই কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে এল থানার কনস্টেবলসহ ওঁর লোকেরা। তখন বুঝলাম পাঁচ পা-ই দেখতে পাচ্ছেন। তাঁকেও বসিয়ে রাখলেন। সব শেষে আমাদের কেস হল। কাগজপত্র দেখালে কর্মচারীরা, আমি শুধু দাঁড়িয়ে রইলাম। তাতেই হয়ে গেল। আমাদের বক্তব্য লিখে নিলেন। ফাইনাল বিচার হবে এখন নয়; এরপরে, সে হবে মাস দুয়েক পর। তখন দোসরা হাকিম আসবেন। এঁর উপরের লোক। আমাকে বললেন—নোটিশ করলে আপনি আসেন না কেন? বললাম- আমি তো এখানে থাকি নে, কলকাতায় থাকি। সংক্ষেপে বললেন-তা হলে কিছুদিন থাকুন এখানে। জমিদারি ভোগ করবেন কলকাতায় বসে বারো মাস, তা অস্তুত সেটেলমেন্ট যতদিন চলছে হবে না। পেশকারকে বললেন—ওঁর সমনগুলো দাও। পেশকার বললে—দাঁড়ান। তারপরই সেই প্রৌঢ় ভদ্রলোকের ডাক হল। হরিদাস মুখার্জি হাজির হো! কনস্টেবল দড়ি ধরে এনে হাজির করলে। হাকিম বললেন-কি? উনি (অর্থাৎ আমি) কলকাতায় থাকেন আপনি তো থাকেন না। এখানেই থাকেন শুনেছি, কাজের মধ্যে নেশা-ভাঙ। তা নোটিশ সমন পেয়েও আসেন না কেন? সাপের পাঁচটা পা গজায়, আপনার কটা গজিয়েছে—দশটা না বিশটা? এবার আমার প্রচণ্ড ক্রোধ হয়েছিল। আমি সমনগুলো হাতে হাতে না নিয়ে চলে এসেছি। পেশকার হাঁকলে, সমন নিয়ে যান। বললাম—যথারীতি বাড়ীতে দিয়ে আসবার নিয়ম অনুযায়ী পাঠিয়ে দেবেন। দেখছি কিছুদিন থাকতে হবে। দেখি। কলকাতায় রঙ-তুলি আনবার জন্য লোক পাঠাচ্ছি। ইতি—
তার কদিন পরেই চিঠি পেয়েছিল—সু, তুমি চিঠির উত্তর দাওনি। খুব পড়ছ বোধহয়। তা পড়। আমি ছবি আঁকছি। এখানে ল্যান্ডস্কেপ খুব ভালো। এবং ছবির দৌলতে অকস্মাৎ সেটেলমেন্ট ক্যাম্প কোর্ট পর্যন্ত রঙ ধরে গেছে। মজা হয়ে গেছে। সেদিন কাঁসাইয়ের ধারে বসে ছবি আঁকছি একমনে। হঠাৎ পিছন থেকে কে বললে—বাঃ! আপনি তো চমৎকার ছবি আঁকেন। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলাম সেই হাকিম হরেন ঘোষ। তখন সাহেব নয়। শৌখীন বাঙালীর ছেলে—পাঞ্জাবি, ফিনফিনে মিলের ধুতি, পায়ে সবুজ রঙের জরিদার নাগরা। মনের রাগ দমন করার অভ্যেস আছে। উঠে হেসে নমস্কার করে বললাম- আপনি! বললেন—হ্যাঁ, বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। দুর থেকে দেখলাম আপনি বসে কি করছেন। কৌতূহল হল। এলাম। আপনি তো চমৎকার আঁকেন! বিনয় করলাম না। বললাম—খুশি হলাম। উনি সিগারেট দিলেন, নিজে ধরালেন। তারপর বললেন—শুনেছিলাম আপনাদের ধনেশ্বরবাবুর কাছে, কল্যাণেশ্বর বলে ইয়ংম্যানটির কাছে, যে আপনি কলকাতায় থাকেন, টাকা আছে বাপের তাই ওড়ান আর থিয়েটার দেখেন, ফুর্তি করেন। আপনি আর্টিস্ট তা তো বলেননি। হঠাৎ খুব হৃদ্য হয়ে বললেন—তাই শুনেই তো রাগ হয়ে গেল মশাই! বললাম—বটে! তাই সমন জারী করেছিলাম। বললাম—তাতে কি হয়েছে? আপনার সমনের টানে এসে কতকগুলো ভালো ল্যান্ডস্কেপ হয়ে যাবে আমার। বললেন—না মশাই, মনটা খচখচ করছে। আপনি গুণীলোক! তবে মনে এটাও হচ্ছে যে ভালই করেছি। আপনাকে তো পেলাম। এখানে মাঠের মধ্যে যা কষ্ট, সারাটা দিন শুধু প্লট নম্বর, বাটা দাগ, রায়তী স্থিতিবান, মোকররী আর এমন এখানকার লোক যে সবটাতেই সকলের আপত্তি। কর রেকর্ড! দেখ কাগজ! এতে আর মাথার ঠিক থাকে! আপনার সমস্ত খতিয়ানে আপত্তি দিয়েছে আপনার জ্ঞাতিরা সে হিসেবে আপনার উপকার করেছি আমি। আমার উপকার করার লাভও হয়েছে দেখছি। এখানে মিশবার লোক পাইনে। আপনাদের ইস্কুললাইব্রেরী থেকে বই আনিয়ে পড়ি। যত পুরনো বই। দিন কাটে না!
মানুষের মন সু, ভারী আশ্চর্য। বুঝলে এখুনি যে লোকটা মন্দ বললে মনে হয় এত বড় পাষণ্ড এবং এত বড় শত্রু আর নেই জগতে, সেই লোকটাই যদি কিছুক্ষণ পর বা তক্ষুনি কথাটা ঘুরিয়ে মিষ্টি কথা বলে প্রশংসা করে তা হলে সব ভুলে মনে হবে লোকটা ভারী ভাল। জান, সত্যটা উপলব্ধি করে খুব আশ্বাস পেলাম। কারণ তোমার আমার মধ্যে তো এরপর মধ্যে মধ্যে ঝগড়া হবেই। আমার তখন নিশ্চয় মনে হবে আজই পালাব, ফকিরী নেব; আর তুমি ভাববে—কি ভাববে? ডাইভোর্স করবে ভাবতে ভাল লাগে না, ভাল লাগে তুমি ভাবছ বিষটিষ খাবে। তখন আমি হয়তো তোমার মুখের দিকে তাকাব, তুমি জলভরা চোখ ফিরিয়ে নেবে। অমনি আমি গিয়ে বলব—আমারই অন্যায়, আমাকে মাফ করো সু! তুমি ফিক করে হেসে ফেলবে। ইতি—
এরপরও খান তিনেক চিঠি লিখেছিল। শেষখানা মনে আছে, তাতে খুব সরস রসিকতা বা বাক্যের ছটা বিস্তার করেনি। লিখেছিল—একেবারে সময় নেই সু। বড় জালের মধ্যে জড়িয়েছি। ধনেশ্বর কাকা আর সুখেশ্বর কাকার ছেলে কল্যাণেশ্বর যে ব্যাপারটা করেছিল তা খুব কঠিন ছিল না, কিন্তু হঠাৎ আমার বড় জ্যোঠামশাইয়ের দুই ছেলে এখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন এবং এমনই কুটিল ব্যাপার করে তুলেছেন যে আমাকে বিপদগ্রস্ত করেছেন। আমাকে পত্তনী বিলি করা সব সম্পত্তিই কেড়ে নেবার ব্যবস্থা করেছেন। আমি প্রাচীন কাগজপত্র হাতড়াচ্ছি। কাগজের ধুলো পেটে গিয়ে গিয়ে পাকা জমিদারি সেরেস্তানবীশ হয়ে উঠছি। রঙ খুব কালো হয়েছে বলছিল গোয়ানপাড়ার হলদী বুড়ী। ইতি—
পুঃ দিয়ে লিখেছিল—সেটেলমেন্ট হাকিমের সঙ্গে প্রেম আবার বিগড়েছে। তার কারণ আমার চেয়ে আমার জ্যাঠতুতো ভাইদের সঙ্গে ওর জমেছে বেশি।—ইতি সু।
তারপর নীরব হয়ে গিয়েছিল সুরেশ্বর। একেবারে নীরব। পুরো একমাস কোন চিঠি পায়নি। অসীমার কাছে খবর নিয়ে জেনেছিল, সুরেশ্বরের এখানকার নায়ের ম্যানেজার হরচন্দ্রের পক্ষাঘাত হয়েছে। ওখানে যে কর্মচারীদের সঙ্গে নিয়ে সুরেশ্বর গিয়েছিল তাকে এখানে পাঠিয়ে সুরেশ্বর ওখানকার কর্মচারীদের নিয়ে মামলা-মোকদ্দমায় প্রায় ডুবে গেছে।
আরও মাসখানেক পর হঠাৎ চিঠি পেয়েছিল সুরেশ্বরের—সেই সাংঘাতিক চিঠি।
সুলতা, বিদায়। বিদায় নিচ্ছি চিরজীবনের মত। সব ভুলে যাও—ভগবানকে ধন্যবাদ, তোমাকে ধন্যবাদ যে বিয়েটা ঘটেনি, তুমিই পরীক্ষার আপত্তি তুলে বিয়েতে রাজী হওনি। হলে আজ আর আক্ষেপের শেষ থাকত না। তুমি আত্মহত্যা করতে। আমার- আমি যা হয়েছি তাই হতাম। অর্ধ পাগল ছিলাম। পুরো পাগল হতে চলেছি। প্রচুর মদ খাচ্ছি। খাঁটি দেশীমতে গোয়ানীজদের তৈরী মদ। আমাকে ভুলে যাও। আমাকে ফেরাবার চেষ্টা কোরো না, তা হলে আমাকে হয়তো আত্মহত্যা করতে হবে! ইতি—
সুরেশ্বর।
কষ্ট সুলতার নিশ্চয় হয়েছিল। তার মা-বাপ কেউই তার এবং সুরেশ্বরের মধ্যে এতটা ঘনিষ্ঠতার কথা জানতেন না। সে রাত্রে ঘরে খিল দিয়ে সারারাত্রি কেঁদেছিল। একবার ভেবেছিল সে নিজে কীর্তিহাট যাবে, দেখা করে মুখোমুখি প্রশ্ন করবে—বল কি ব্যাপার! কেন এ চিঠি লিখেছ? কেন? কিন্তু ভাবলেও তা কাজে করতে পারেনি। মনে হয়েছিল, তার থেকে বোধহয় মেয়ের পক্ষে মৃত্যু ভাল। নিজে যাবে সে উপযাচিকা হয়ে তাকে সাধতে! ছি-ছি-ছি! ওদিকে ভাগ্যক্রমে ওদের স্টুডেন্টস মহলে ছাত্রআন্দোলন উঠেছিল জমে। তারই মধ্যে পড়েছিল সে ঝাঁপ দিয়ে। তারপর বের হল পরীক্ষার খবর। এই খবরটাই তাকে শুধু বাঁচিয়ে দিলে না, উৎসাহে তার মাথাটা উঁচু করে দিয়ে বললে—বেঁচে গেছ। চল, সামনে চল। বি.এ. পরীক্ষার ইকনমিক্সের অনার্স ফার্স্ট ক্লাস সেকেন্ড হয়েছে। প্রবল উৎসাহে সে এম.এ. পড়তে শুরু করলে। যেদিন এম.এ. ক্লাসে ভর্তি হয় সেইদিনই সে দাঁড়িয়ে ছিল ধর্মতলার মসজিদটার কাছে, ধর্মতলা স্ট্রীটের ফুটপাথের উপর, অপেক্ষা করছিল ট্রামের জন্য। হঠাৎ তার সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল সুরেশ্বরের সঙ্গে।
সুরেশ্বরের গৌরবর্ণ রঙের উপর একটা পোড়া দাগের মত ছোপ ধরেছে। পরনে তার সেই বিচিত্র অদ্ভুত সাজ আরও অদ্ভুত হয়েছে। গেরুয়া রঙের সিল্কের একটা আলখাল্লা গোছের জামা। পরনে কোঁচানো ধুতি। মুখে একমুখ দাড়ি-গোঁফ, বাবরী চুল, চোখে- স্বপ্নাতুরই হোক আর উদ্ভ্রান্তই হোক—একটা বিচিত্র দৃষ্টি, সে বেরুচ্ছে লাহাদের দোকান থেকে। তার পিছনে একটা লোকের মাথায় একগাদা জিনিস —সম্ভবত ছবির জন্য তৈরী ক্যানভাস। লোকটার হাতেও একটা কাঠের বাক্স, তাতে বোধহয় তার্পিন—বার্নিশ রঙের টিন ছিল। সুরেশ্বরের নিজের হাতে একটা প্যাকেট। সম্ভবতঃ রঙ-তুলি। ভাগ্যক্রমে বেরুবামাত্র দুজনেই দুজনকে দেখতে পেয়েছিল, চোখাচোখি হয়েছিল। সুলতার চোখ বিস্ফারিত দীপ্ত হয়ে উঠেছিল। সে-ও মুহূর্তদুয়ের জন্য থমকে দাঁড়িয়েছিল, সুলতার চোখের সঙ্গে মিলিত হওয়া তার চোখের দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে পারেনি। কিন্তু ওই দুই মুহূর্ত পরেই সে মুখ ফিরিয়ে হনহন করে চলতে শুরু করেছিল পশ্চিমমুখে এগিয়ে। ইতিমধ্যে এসে গিয়েছিল। একখানা ট্রাম। দাঁড়িয়েছিল দু ফুটপাথের মাঝখানে আড়াল করে। সে ট্রামে সুলতা চড়েনি। ট্রামখানা চলে গেলে সে তাকিয়ে তাকে খুঁজেছিল। তখন সুরেশ্বর আর নেই। পরের ট্রামে সে ইউনিভারসিটি এসেছিল। কিন্তু সন্ধ্যায় তাকে ফোন করেছিল। ধরেছিল চাকর। সে নাম বলেছিল, বলেছিল—বল বাবুকে সুলতা ঘোষ ডাকছেন। সে শুনতে পেয়েছিল সুরেশ্বর বলছে—বল বাবু বাড়ী নেই। উত্তরটা সে আর চাকরের মুখে শোনার জন্য প্রতীক্ষা করেনি। রিসিভারটা রেখে দিয়েছিল। ঘৃণা হয়েছিল তার।
কারণটা জানতে তার দেরী হয়নি।
অসীমা তাকে বলেছিল—সুরোদার খবর শুনেছিস?
—কি?
—সেখানে প্রবল প্রতাপে জমিদার হয়ে বসেছে। মদ খাচ্ছে। দেশী মদ। বাবা বলেছিলেন—ভাল উপমা দিয়ে বললেন—বুনো মোষ যেমন পাঁকজলে গলা ডুবিয়ে বসে, তেমনি ভাবে ডুবেছে শুনছি।
সুলতা বলেছিল—ওর চেয়েও ভাল উপমা আছে অসীমা। বন্য শূকরের উপমা। তারা শুধু গা ডোবায় না। দাঁতসুদ্ধ মুখ ডুবিয়ে পাঁক আর গেঁড়ো তুলে খায়।
উত্তরে কিছু বলতে যাচ্ছিল অসীমা। কিন্তু সুলতা চলে গিয়েছিল। বলেছিল—কি করব শুনে অসীমা। আজ আমার ক্লাসের পর ক্লাস। তারপর ইউনিয়নের মিটিং।
এম.এ. পরীক্ষার সময় সে শুনেছিল সেবার ফাইন আর্ট এগজিবিশনে সুরেশ্বর রায় একখানা ছবির জন্য ফার্স্ট প্রাইজ পেয়েছে। ছবিখানার নাম মা-যশোদা। একটি শ্যামাঙ্গী তরুণী মায়ের কোলে ছেলে আর আকাশে চাঁদ। ছবিতে এক সময় আগ্রহ ছিল। কিন্তু সে আগ্রহ তার বোধ করি বিদ্বেষে পরিণত হয়েছিল সেবার
অসীমা গিয়েছিল সুরেশ্বরের সঙ্গে দেখা করতে। অসীমার সেবার ফিথ ইয়ার। ফিরে এসে সুলতাকে ফোন করেছিল—সুরোদা বিলেত যাচ্ছে সুলতা।
বিলেত? তা ভাল। ওই কীর্তিহাটের জমিদারী থেকে ভাল। কিন্তু খবরটা আমাকে কেন? -এমনি। তোকে একটা জিনিস দিয়েছে দিতে।
—আমাকে?
—হ্যাঁ। একখানা ছবি। খুব সুন্দর একটা ল্যান্ডস্কেপ!
—ধন্যবাদ জানাস। কিন্তু আমার ঘরে ছবি টাঙাবার জায়গা নেই। ফিরিয়ে দিস।
—ফিরিয়ে দেব?
—হ্যাঁ। বলে সে রিসিভার নামিয়ে রেখেছিল। তারপর পড়ায় মন দিয়েছিল। যেন এই ছোট্ট ঘটনাটা তার পড়ার ঝোঁকে বেশ খানিকটা জোর জুগিয়েছিল দু-চার দিনের জন্য।
সেবার এম.এ. পরীক্ষায় সুলতা হয়েছিল ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট। বাবা-মা বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, মেয়েকে সংসারী দেখতে চেয়েছিলেন তাঁরা, কোন বাবা-মা তা না চায়, কিন্তু তার ছাত্রী-জীবনের এই সাফল্য এখানেও তাকে তার স্বাধীন মতে চলবার পাশপোর্ট দিয়েছিল। সে চাকরী পেয়েছিল, ভাল চাকরী, গভর্নমেন্ট ডেকে তাকে শিক্ষা বিভাগে বেথুন কলেজে ইকনমিক্সের লেকচারার করে নিয়েছিল। এবং কিছুদিনের মধ্যেই পদোন্নতি হবে এ আশ্বাসও ছিল। নিজেকে কাজে ডুবিয়ে দিয়েছিল পরমোৎসাহে। নিজেকে বিচার করে সুলতা দেখেছে। তাতে বুঝেছে সুরেশ্বরের প্রতি অনুরাগ এর হেতু নয়। আজকালকার নারী-স্বাধীনতার যুগেও মনের অ্যাডোলেসেন্সের একটা কাল আছে; সে কালের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে কিছু তরুণ বন্ধু কিছু কিছু স্বপ্নসঞ্চার করে, কিন্তু সে স্বপ্নই। স্বপ্ন দুভাবে মিলোয়—এক, কিছুক্ষণ বেশ গল্পের মত বাস্তবের ধারাবাহিকতা রেখে চলে কেমন এলোমেলো হয়ে যায়, তুলির হিজিবিজি দাগ টেনে মিশিয়ে আঁকা ছবি দুর্বোধ্য করে দেওয়ার মতো। অথবা কোন রচনার অংশবিশেষের উপর কলমের দাগ টেনে কেটে দেওয়ার মত। আর একভাবে শেষ হয়, ঘুম ভেঙে গিয়ে স্বপ্নস্বপ্ন অর্থাৎ মিথ্যে বলে ব্যঙ্গ করে মিলিয়ে যায়। সে স্বপ্ন শেষ পর্যন্ত হিজিবিজি হয়ে বা অবান্তর অবাস্তব হয়ে স্বপ্নের মধ্যেই অর্থহীন হয়, তাতে বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্ন থাকে না, শুধু হাসি পায়। কিন্তু যে স্বপ্ন ধারাবাহিকতায় বাস্তবের পথে চলতে চলতে ঘুম ভেঙে থেমে যায় ভেঙে যায় সেই স্বপ্নই স্বপ্নকে মুখ ভেঙচায়, এবং স্বপ্ন যে দেখে তাকেও ভেঙচায় এই বলে যে কেমন ঠকেছ! তাতেই হয় খেদ, তাতেই স্বপ্নকে ব্যঙ্গের বিষয় করে তোলে। সুরেশ্বরের সঙ্গে তার জীবনের এই ঘটনাটুকু পরিসরে ক্ষুদ্র হলেও ধারাবাহিকতায় এবং ঘটনাবিন্যাসে অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং বাস্তব ছিল, সেটা এইভাবে হঠাৎ ভেঙে গেল, ঘুম ভেঙে স্বপ্ন অসমাপ্ত হয়ে শেষ হওয়ার মত। যার ফলে যে কোন অন্য পুরুষের প্রতি এবং প্রেমের প্রতিও তাকে বিমুখ করে তুললে। সঙ্গে সঙ্গে প্রেমের বদলে সে চাকরী এবং ঘরকন্নার বদলে চাকরীর সঙ্গে রাজনীতির বৃহত্তর জীবন ও জগতের রঙ্গমঞ্চে বেশ বড় পার্ট পেয়ে গেল। তাতেই মেতে উঠল। তখন ১৯৩৯ সাল। পৃথিবী এবং তার সঙ্গে ভারতবর্ষের রাজনীতিতে বলতে গেলে পুরনো অঙ্ক শেষ হয়ে নতুন অঙ্ক শুরু হচ্ছে। যার গতি যার আবেগ—নাটকের ভাষায় টেম্পো-একেবারে গোমুখীতে গঙ্গাবতরণের মত। স্বর্গের মন্দাকিনী পৃথিবীর মাটিতে ঝরে পড়ে তার জলে ধুলো, মাটি, খড়কুটো সবকিছু স্বীকার করে কলস্বরে ঘোষণা করছেন-গঙ্গা হলেও আমি জল, গতি আমার নিম্নগামিনী, বিষ্ণু-পাদোদ্ভূতা হয়েও আমি মাটিকে ভালবাসি, আবিলতাকে স্বীকার করি! এই সত্য এই বাস্তব।
ইয়োরোপে তখন যুদ্ধ বাধে বাধে অবস্থা। চীন জাপান যুদ্ধে নেমে গেছে। ভারতবর্ষের রাজনীতিতে বামপন্থা প্রবল হয়ে উঠেছে। সশস্ত্র বিপ্লববাদীরা সোস্যালিজম কম্যুনিজম নিয়ে প্ল্যান করছে। নেতাজী সুভাষচন্দ্র তখন সুদ্ধ সুভাষচন্দ্র-ভারতের বিদ্রোহী আত্মার নবযৌবনের প্রতীক; তিনি কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছেন। কিন্তু দক্ষিণপন্থীদের দৃষ্টি এবং পদক্ষেপের মন্থরতার সঙ্গে তাঁর দৃষ্টি এবং পদক্ষেপ মিলছে না। সেই কালে পৃষ্ঠপোষকতায় এবং প্রেরণায় সুলতা কিছুদিনের মধ্যেই প্রায় নেত্রীস্থানীয় হয়ে উঠল। বাংলার নবীনা নেত্রী যাঁরা—কমলা দাশগুপ্তা, বীণা দাশ, মায়া ঘোষ প্রভৃতি মন্দিরা কাগজকে কেন্দ্র করে সমবেত হন—সে দলে সে ঠাঁই করে নিলো। এরই মধ্যে একদিন দেখা হয়ে গেল সুরেশ্বরের সঙ্গে। দেখা হল না—সে-ও তাকে দেখলে—সুলতাও তাকে দেখলে। হাওড়া স্টেশনে বম্বে মেল ছাড়ছিল-সন্ধ্যেবেলা- সুলতা গিয়েছিল হাওড়া স্টেশনে, তার বান্ধবীকে তুলে দিতে অন্য একটা গাড়ীতে। হঠাৎ সে দেখলে কুলীর মাথায় মোটঘাট চাপিয়ে নিখুঁত সাহেবী পোষাক পরা সুরেশ্বর চলেছে। মুখোমুখি প্রায়; দুজনেই থমকে দাঁড়িয়ে গেল। দুটি কথা হয়েছিল। সুরেশ্বর বলেছিল—বিলেতে যাচ্ছি। সুলতা বলেছিল—গুড লাক! বলে সে-ই আগে পাশ কাটিয়ে অন্য প্ল্যাটফর্ম-মুখে চলে গিয়েছিল। সুরেশ্বর কি করেছিল ফিরে তাকিয়েও দেখেনি, তবে সে যে বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেনি এটা সে অনুমান করেছিল। সে হয়তো মুহূর্তখানেক দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরিয়ে মেলের রিজার্ভ করা ফার্স্ট ক্লাস বার্থে গিয়ে চেপে বসেছিল।
কাগজে দেখেছিল—হঠাৎ নজরে পড়েছিল—বিলেতে তার একখানা ছবির খুব প্রশংসা হয়েছে। ‘ইন্ডিয়ান ম্যাডোনা’। কাগজে লিখেছিল—এই ছবিখানাই কলকাতার প্রদর্শনীতে বিশেষ সম্মান এবং প্রশংসা পেয়েছিল।
তাতেও তার অর্থাৎ সুলতার জীবনযাত্রার স্বচ্ছন্দ গতি কোন বেদনাদায়ক স্বপ্নের দ্বারা বিঘ্নিত হয় নি। সহজভাবে স্বচ্ছন্দ গতিতে সে-ও কাগজখানা পুরনো খবরের কাগজের সঙ্গে বিক্ৰী করে দিয়ে এগিয়ে চলেছিল আপন পথে—কলেজে, কাগজের আপিসে। পার্টি আপিসে অবশ্য সে যেত না; সেটা সরকারী চাকরীর বাধা-নিষেধের জন্য।
তারপর, গঙ্গায় অনেক জল বয়ে গেছে—এ কথাটাও ‘যৎকিঞ্চিৎ’ হয়ে গেছে ব্যঞ্জনা হিসেবে। ভাগীরথীর মুখেই চড়া পড়েছে। এতদিনে সত্য করে গঙ্গার ধারা দুটো হয়ে গেছে দুটো দেশে। ভাগ করে দিয়ে ইংরেজ যখন দেশত্যাগ করল, তখন ভাগীরথীর বুকে জাহাজ ভাসিয়ে ডায়মন্ডহারবার হয়ে যেভাবে বাংলা দেশে এসে কলকাতার পত্তন করেছিল—কুঠী গেড়েছিল, সেভাবে এদেশ ত্যাগ করেনি। ভাগীরথীর মুখেও চড়া পড়েছে। তারা দলে দলে ১৯৪৭। ৪৮ সালে দমদম এরোড্রোম থেকে প্লেনে উড়ে চলে গেছে; ইংরেজ পল্টনেরা গেছে বম্বেতে ইন্ডিয়া গেটের ভিতর দিয়ে বম্বে ডকে জাহাজে চেপে।
বাংলাদেশে প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ মুখ্যমন্ত্রী হলেন। তখন রাজনৈতিক ক্যারামবোর্ডে দলাদলির স্ট্রাইকারের ধাক্কায় কর্মীরা বিভিন্ন দলের পকেটে ঘাঁটি গাড়ছে।
কম্যুনিস্টদের সঙ্গে সুলতার মিল ১৯৪২ সাল থেকেই নেই। অর্থাৎ জনযুদ্ধের আমল এবং অ্যান্টিফ্যাসিস্ট লেখক-শিল্পীদের আন্দোলনের আমল থেকে। সে অর্থনীতির সঙ্গে রাজনীতি বিজ্ঞানের দৃষ্টি পেয়েছে। সে এসবের তত্ত্ব এবং মর্ম বুঝত। গোড়া থেকে সে সোস্যালিস্ট। তখনও পর্যন্ত সোস্যালিস্টরা কংগ্রেসের মধ্যেই ছিল-সে-ও ছিল—তবে একই বোর্ডের চারটে পকেট হওয়ায় একটা পকেটেই স্থান করে নিয়েছিল। তারপর প্রফুল্ল ঘোষ মন্ত্রিত্ব ছাড়লেন। ডা. বিধান রায় মুখ্যমন্ত্রী হলেন। প্রদেশ কংগ্রেসেও ওলোটপালোট হল। অতুল্য ঘোষ প্রেসিডেন্ট হলেন। মহাত্মাকে হত্যা করলে গডসে দিল্লীর বিড়লা ভবনে। তারপর ঐক্যের বন্ধন দেখতে দেখতে ছিন্ন হয়ে গেল। সোস্যালিস্টরা পৃথক হল। তার সঙ্গে সঙ্গে সুলতাও। তারপর একান্ন সালে ইলেকশনের আগে কৃষক-প্রজা পার্টি হল। প্রফুল্ল ঘোষ তার বাংলাদেশের নেতা- সর্বভারতীয় প্রধান হলেন আচার্য কৃপালনী। ইলেকশন হয়ে গেল। সোস্যালিস্ট-কৃষক-প্রজা এক হয়ে পি-এস-পি হল!
দেশকে দেশের মানুষকে তীব্র আক্রমণ না করে পারলে না সুলতা। মানুষগুলো অদ্ভুত বোকা। এরা ধরতেও পারলে না কংগ্রেসের পরিবর্তন। তার ধাপ্পাবাজি! তারা ভোট দিলে কংগ্রেসকেই। কংগ্রেসকে এই সাবাস সুলতা দেয় যে, কংগ্রেস এই বোকা মানুষগুলোকে ঠিক চিনেছে। তারা যেখানে যেমন সেখানে তেমন খেলা খেললে। যেখানে জমিদারকে দাঁড় করালে ভোট পাবে, সেখানে জমিদারকে দাঁড় করালে। যেখানে শেঠকে দাঁড় করালে টাকার জোরে জিতে যাবে, সেখানে তাই করল। যেখানে কর্মী দিতে হবে, সেখানে কর্মীই দিল। এবং এই কৌশলে অধিকাংশ পল্লীঅঞ্চলেই জিতে গেল। দু-চার জায়গায় হার হ’ল না তা নয়—তবুও তারা সংখ্যায় এমন মেজরিটি হল যে, সব দলগুলি তাদের মতবাদ এবং নিজেদের সততা ও বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে যথেষ্ট গৌরব এবং বিশ্বাস পোষণ করেও মানুষের কাছে গৃহীত হল না। তবে এটা ঠিক কথা যে-অন্ততঃ সুলতাদের তাই বিশ্বাস—এই যাত্রাদলের রাজার সাজ—যা প’রে কংগ্রেসওয়ালারা আসর জমাচ্ছে-সে আসর ভাঙবেই। জীবনের আসর চিরদিনের, সত্যের কদর চিরদিনের, কিন্তু জীবনের নামে অভিনয়ের আসর যতই অভিনয়গুণে জীবন্ত হোক, অভিনয় শেষ করতেই হয়। তখন পালাটা আর সত্য থাকে না এবং পালার বীরগুলো তখন একান্তভাবে নট বলে ধরা পড়ে। তখন সত্য এবং সত্যকারের মানুষের কাল আসে; তাদের তখন চেনে মানুষ—তাদের ডেকে এনে বসায় জীবনের আসরে। কথাটা আরও জোর দিয়ে বললে সে—পঞ্চাশ সালটা গোটা বিলেত এবং ইউরোপ ঘুরে এসে। স্টেট থেকেই স্কলারশিপ পেয়েছিল সে।
১৯৫৩ সালের নভেম্বর সেশনে কংগ্রেস দল নাটুকে ভাঁওতা দিলে দেশের মানুষকে জমিদারী উচ্ছেদ বিল এনে। জমিদারী উচ্ছেদ বিল নয়, এস্টেটস্ এ্যাকুইজিশন বিল। শুধু দেশের মন্ত্রিত্ব নিয়ে তৃপ্তি হচ্ছে না এদের—জমিদারদের জমিদারী কিনে প্রকারান্তরে তারা জমিদারই সেজে বসবে। প্রজার খাজনায় এক পয়সা মকুব হবে না, ষোল আনা লাভ সমেত আয়বৃদ্ধি হবে। পতিত জমি-যা জমিদারদের খাস—তা আসবে তাদের হাতে—তারা বিলি করবে ইচ্ছামত। বিনিময়ে ভোগের সুবিধে হবে বটে।
বিল যেদিন থেকে বিধানসভায় এসেছে সেদিন থেকেই সে প্রায় নিয়মিত আসছে- শুনছে বক্তৃতা। অভিনয় দেখছে। কিন্তু একদিনও সে সুরেশ্বরকে দেখে নি। এবং এমনই ভাবে সে তার মন থেকে স’রে বা মুছে গেছে যে, তার দেখা এখানে পেতে পারে এমন কথা তার মনে হয় নি। এর অবশ্য আরও একটা কারণ আছে। সেটা এই যে, সুরেশ্বর দেশে ফিরে-সে সেই ৪১ সালে—আবার সেই কীর্তিহাটেই ফিরে গেছে। সে তার খোঁজও করেনি কোনদিন এবং কোন সংবাদও সে পায়নি যাতে তাকে মনে করবার হেতু হতে পারে। না শিল্পী হিসাবে না মানুষ হিসাবে। অসীমা সীমার বিয়ে হয়ে গেছে। তারা ঘরণী গৃহিণী—অবশ্য ভাল ঘরেরই। তারাও তাকে ভুলেছে—সেও তাদের ভুলেছে। দেখাও হয় না। চিঠি লেখালিখিও নেই। তা ছাড়া আর একটা পার্থক্য হয়েছে সেটা সীমা-অসীমার ভাইকে নিয়ে। প্রদীপ যৌবনে পা দিয়েই বিয়াল্লিশ সাল নাগাদ গিয়ে পড়েছিল অ্যান্টিফ্যাসিস্ট রাইটার্স-আর্টিস্টস্ এ্যাসোসিয়েশনে। সেখান থেকে একেবারে কম্যুনিস্ট পার্টিতে। দীর্ঘদিন স্টুডেন্টস ফ্রন্টে স্টুডেন্ট লীডার হয়ে ছাত্রজীবনের জের টেনে অবশেষে অ্যাডভোকেট হয়েছে হাইকোর্টে। পার্টির মেম্বারও সে বটে। কম্যুনিস্ট পার্টি ১৯৪৯। ৫০ সালে বে-আইনী ঘোষিত হলে অনেকদিন জেলেও ছিল। জেল থেকে বেরিয়ে সে হাইকোর্ট যাচ্ছে আসছে। এর মধ্যে রাশিয়া-চীন দুটো দেশেই ঘুরে এসেছে। তার সঙ্গে চীনে গিয়েছিল অসীমা আর তার স্বামী—রাশিয়া গিয়েছিল সীমা এবং তার বর। তারা দুই বোনেই বিলাসিনী ধনী গৃহিণী হয়েও এবং পার্টি মেম্বার না হয়েও খুব কড়া রকমের কম্যুনিস্ট মতবাদ পোষণ করে। সুতরাং তাদের সঙ্গে টেলিফোনে কথা হওয়া দূরের কথা—পথে দেখা হলেও এদিক ওদিকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং গগলসটা অকারণে দুহাত দিয়ে নাকের উপর টিপে বসায় অর্থাৎ সুরেশ্বরের সংবাদ কোন একটি সুচীছিদ্র সরু পথেও কোন সুত্রে আসে নি, আসতে পায় নি। সুতরাং এস্টেটস্ এ্যাকুইজিশন বিলের শেষদিনে সে যখন পরম কৌতূহলভরে উপরনিচে জমিদারদের মধ্যে কুমার বিমলচন্দ্র সিংহকে দেখে, তারপর বর্ধমানের মহারাজার টুপি খুঁজে দেখতে গিয়ে পেল না, তখন আর কাউকে খোঁজে নি-সুরেশ্বরকে মনেও পড়ে নি। শুধু একটা কৌতুককর কথা মনে হয়েছিল। মনে হয়েছিল, আজ যদি ভূমিরাজস্বমন্ত্রী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর জায়গায় দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের বংশধর কুমার বিমলচন্দ্র সিংহ থাকতেন তো বড় ভাল হত। তাহলে অপোজিশনের কেউ না কেউ তাঁর কৌতুককথাটা নিশ্চয় বলত। অন্তত সে শ্রীসুধীর রায়চৌধুরীকে, দাশরথি তা’কে বলে দিয়ে আসত বলতে। বলত —দেড় শো বছর পরে আবার হেস্টিংস আর তাঁর দেওয়ান রায়রাঁইয়া নতুন খেলা খেলতে এসেছেন।
গালাগাল, তীব্র সমালোচনা, কঠিন উক্তি, গোলমাল করে বিপক্ষ দলের বক্তৃতায় বাধা দেওয়া, বক্তৃতা ঢেকে দেওয়া হয়ে গেছে। আজ শেষদিনে এই হলে ঢুকে ওই কথাটা মনে করেও সে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ভুলে গেল। মনের মধ্যে একটা গম্ভীর ভারী থমথমে কিছু জুড়ে বসল। এ দেশের ইতিহাস স্মরণ করে মনে হ’ল—যাই গলদ থাক নতুন আইনে, আজ এর গুরুত্ব এর মহত্ত্ব এর বিপ্লবাত্মক সম্ভাবনাকে কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। মনের মধ্যে তার হঠাৎ মনে হল একটা দেড়শো বছরের পাকা ইমারতের তলায় ডিনামাইট চার্জ করা হয়েছে—যে মুহূর্তে স্পীকার বলবেন—It is now agreed to and passed; সেই মুহূর্তে বিপুল বিস্ফোরণ শব্দের সঙ্গে বিরাট ইমারত টলতে টলতে চারিপাশে ফেটে চৌচির হয়ে বিপুলতর শব্দ করে মাটিতে আছড়ে পড়বে। বিরাট একটা ধূলির পুঞ্জ উঠবে আকাশে, ঢেকে দেবে চারিদিক। হয়তো চাপা পড়ে মানুষ কাতরাবে ধ্বংসস্তূপের ভিতর থেকে। শুনতে হবে দাঁড়িয়ে। চোখে জল এলেও মুছে ফেলতে হবে। যারা ওই ঘর আঁকড়ে পড়েছিল মৃত্যুই তাদের নিয়তি। মরতে দাও তাদের। তারা মরুক। খেদ কিসের? তাকাও, দৃষ্টি আরও প্রসারিত করে তাকাও; স্মরণ কর; এই তো কিছুদিন আগেই গোটা করদ রাজ্যগুলি অসহায়ভাবে এমন করেই ভেঙে পড়েছে! মনে পড়ছে না হায়দ্রাবাদে নিজামের নিজামত্বের সব থেকে উঁচু মিনারটা ভেঙে পড়ে যাওয়ার ছবি? কেঁদো না।
ভাবছিল সে। এরই মধ্যে কারুর মোটা ভারী গলার শব্দে সে চমকে উঠল। ডা. রায়ের গলা। তিনি তাঁর শেষ বক্তৃতা দিতে উঠেছেন। সম্ভ্রমভরেই সে তাঁর দিকে তাকালে। অস্পষ্ট গোটা হাউসে কোথাও অসম্ভ্রম ছিল না। সকলে ডা. রায়ের গুরুত্ব পূর্ণ স্বীকার করে গম্ভীরভাবে তাঁর দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। ডা. রায় আরম্ভ করলেন—
“Sir, the curtain is about to be rung down on the scene with which-we in Bengal have been familiar for the last ।50 years.”
হ্যাঁ, তাই মনে হচ্ছে। বেশ বলেছেন। যবনিকা নেমে আসছে। জমিদারদের নাটমন্দিরে, জলসাঘরে, উৎসব-সমারোহের আলোকোজ্জ্বল দৃশ্যের শেষে যবনিকাপাত হচ্ছে! জমিদারেরা এবার মুখের রঙ তুলে জরির পোশাক ছেড়ে পথে এসে দাঁড়াবেন। এতক্ষণে হঠাৎ মনে পড়েছিল সুরেশ্বরকে। কীর্তিহাটের বাড়ী চাপা পড়বে সে? না বেরিয়ে এসে পথে দাঁড়াবে?
সে চিন্তা বেশিক্ষণ থাকেনি। ডা. রায়ের গম্ভীর কণ্ঠের বক্তব্য স্তব্ধ বিধানসভার গম্বুজের গোল ছাদে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল, একটানা তিনি বলে চলেছিলেন—একটিবারের জন্য কোন কথা কেউ বলেনি অন্য কোন শব্দও হয়নি।
“I am glad to say that my Party has been able to put before the country to-day a scheme which, I hope, will lead to better understanding between the raiyats and the landlords, between different classes of society in this country and I hope that this will lead to the establishment of what we earnestly desire namely a welfare state in Bengal.”
শেষ করলেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস তরফ থেকে শুরু হয়ে সারা সভায় সঞ্চারিত হয়ে ধ্বনিত হয়ে উঠল টেবিল চাপড়ানো শব্দ—যা করতালি ধ্বনি বলে গণ্য। বেশ লাগল। হাসিমুখেই উঠে দাঁড়াল সুলতা। শুধু দুটি শব্দে তার আপত্তি আছে। My Party কেন? শুধু My Party কেন? জমিদারী প্রথা উঠবে এতে কার আপত্তি ছিল—কে না চেয়েছিল? এ যে বাংলাদেশের মাটির ভেতর থেকে বাংলাদেশ চেয়েছিল।
হাসতে হাসতে বেরিয়ে এসে সে লবীতে দাঁড়াল। দলে দলে এম.এল.এ.-রা এখনও বিতর্ক করছেন। কিছু কিছু প্রবীণ সভ্যেরা বেরিয়ে যাচ্ছেন। নিচে গাড়ী এসে দাঁড়াচ্ছে। নিজের নিজের গাড়ীতে উঠে চলে যাচ্ছেন। ওদিকে ওপর থেকে সিঁড়ি ভেঙে দর্শকেরা নামছেন। চিনি-চিনি করেও যেন কয়েকজনকে চেনা গেল না। মহারাজ শ্রীশচন্দ্র নন্দী নামলেন। বামপন্থীরা তাঁর দিকে তাকিয়ে কণ্ঠশ্বর একটু মৃদু করলেন। কয়েকজন নমস্কার করলেন—শ্রীশ নন্দীও মৃদু হেসে নমস্কার করলেন।
একজন খবরের কাগজের রিপোর্টার তাঁর কাছে দাঁড়িয়ে বললে—একটা কথা জিজ্ঞাসা করছিলাম স্যার।
—বলুন।
—এই বিল সম্বন্ধে আপনার মত!
—নিশ্চয় খুব ভাল! ডিটেলস নিয়ে হয়তো একটু-আধটু পার্থক্য থাকতে পারে।
—একটু বেশী করে
—ওই খুব বেশী যথেষ্ট। খুব ভাল। দেশের লোক যখন চেয়েছে। এবং জমিদারেরাও বাঁচল। ওদিকে পিছন থেকে সরস কণ্ঠে কেউ বললে-অন্ততঃ গালাগালের হাত থেকে। তিনি আর কেউ নন-তিনি কুমার বিমলচন্দ্র সিংহ। তাঁর কণ্ঠস্বর সুপরিচিত।
শ্রীশচন্দ্র নন্দী নেমে গেলেন—তাঁর গাড়ী এসে লেগেছে। বাইরে কম্পাউন্ডে গাড়ীর হর্নে রাত্রি চকিত হয়ে উঠেছে—হেডলাইটের আলোগুলো বাগানের গাছের মাথায় মাথায় ঘুরছে বাঁক নেবার সময়।
কুমার বিমলচন্দ্র সিংহ একজন বামপন্থী নেতাকে বললেন—আপনার স্পীচ যাকে বলে টাইগারি স্পীচ হয়েছে। ওয়ান্ডারফুল! সন্দেহ হচ্ছিল নিজের চরিত্রে। খুব বলেছেন লাম্পট্য টাম্পট্য লাগিয়ে—! হেসে উঠলেন। বেড়ে বলেছেন। তা চলুন না, চা খেয়ে গল্প ক’রে যাবেন বাড়ী।
—আজ না।
—বেশ, তা হলে কবিয়াল গোমানী আর লম্বোদরকে ডেকে আসর পাতাই একদিন। একজন জমিদার একজন লেফটিস্ট লীডার—আপনার স্পীচের জবাব সেখানে পেয়ে যাবেন। কি বলেন!
—মোস্ট গ্ল্যাডলি! তবে কান্দীর মিষ্টি খাব। মনোহরা।
—তার সঙ্গে লবণাক্ত কিছু? আপত্তি হবে না তো?
ভদ্রলোক বললেন-নিশ্চয় না। গাল দিয়েও আপনার গুণ গাইব।
ঠিক এই সময়টিতেই এসে সামনে দাঁড়াল দীর্ঘকায় একটি লোক। প্রথমে চিনতে পারেনি সুলতা। চোখে নীল চশমাটার জন্যে আর ওকে এখানে দেখতে পাবার সম্পর্কে সচেতনতা না থাকার জন্যই চিনতে পারেনি। তবে রোগাও হয়ে গেছে সে। শীর্ণ দেখাচ্ছে। দাড়ি গোঁফ না থাকাটাও একটা কারণ বটে। গায়ে ঢিলেঢালা আলখাল্লা গেরুয়া সিল্কের। পরনে পাজামা। সুরেশ্বর তার সামনে থমকে দাঁড়াল। সুলতা তখনও তাকিয়ে ছিল তার নীল চশমাটার দিকে, কারণ চশমাটা যেন তার মুখেই নিবন্ধ। কে? ভাবছিল সুলতা।
চোখের চশমাটা খুলে সুরেশ্বর বললে—চিনতে পারছ না?
সুলতা সবিস্ময়ে বলে উঠল—তুমি? তার বিস্ময় তাকে উষ্ণ হয়ে উঠবারও অবকাশ দিলে না।
হেসে সুরেশ্বর বললে—হ্যাঁ।
সকৌতুকে এবার সুলতা বললে—জমিদারির উপর যবনিকাপাত দেখতে এসেছিলে?
সুরেশ্বর হাসলে, বললে—হ্যাঁ।
সুলতা বললে—তা যবনিকাপাতের সঙ্গে পালচাপা পড়নি। কংগ্রেস সুবিধে দিয়েছে, গ্রীনরুমে গিয়ে কম্পেনসেশনের টাকায় মেক-আপ বদলে এবার নতুন সাজে রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হতে পারবে। এবার কি হবে? কংগ্রেসী, না বিজনেস ম্যাগনেট? তা ছাড়া তোমাদের তো আরও সুবিধে, দেবোত্তর। এবার আর নায়েব গোমস্তা পাইক রেখে প্রজা ঠেঙিয়ে খাজনা আদায় করতে হবে না। খোদ সরকার এবার অ্যানুয়িটি পৌঁছে দেবেন!
সুরেশ্বরের হাসি এতেও মিলিয়ে গেল না। সে কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু ওদিক থেকে কুমার বিমলচন্দ্র সিংহ সুরেশ্বরকে দেখে বললেন—কি মশাই, আপনি কীর্তিহাটের সুরেশ্বর রায় নয়? শিল্পী সুরেশ্বর রায়?
সুরেশ্বর নমস্কার করে বললে—হ্যাঁ। আপনি ভাল আছেন?
—হ্যাঁ, তা আছি। উপায় কি ভাল না থেকে? তারপর আপনার খবর কি? বিলেতে গিয়ে নাম কিনে দেশে এলেন। তারপর সব নীরব। তবে শুনি না কি দেশে বসে দেদার ছবি আঁকেন। তা আমাদের দেখান!
—দেখাব।
—হ্যাঁ। এগজিবিশন করুন।
—এগজিবিশন নয়। কয়েকজন রসিক এবং আপনজনকে দেখাব।
—বেশ। আমাকে বাদ দেবেন না।
—নিশ্চয়ই না!
—আচ্ছা চলি।
তাঁর গাড়ী এসে লেগেছে। তিনি চলে গেলেন।
সুলতা যেতে যেতে থমকে দাঁড়িয়েছিল। বললে—আমাকে দেখাবে না?
—ছবি?
—হ্যাঁ।
—যদি বলি আজই চল। তোমাকেই সর্বাগ্রে দেখাবার বাসনা আমার ছিল। এখানে না পেলে আমি তোমার বাড়ী যেতাম। কারণ ছবি ঠিক এগজিবিশন নয়। ছবির মধ্যে দিয়ে আমার জবানবন্দী।
বিস্মিত হয়ে সুলতা তার মুখের দিকে তাকালে। এদিকে লবী জনবিরল হয়ে এসেছে। যাঁরা ও আছেন তাঁরা নেমে গিয়ে বাগানে গিয়ে কে কার গাড়ীতে যেতে পারেন দেখছেন। কিছু কিছু দল বেঁধে হেঁটে বেরিয়ে পড়ছেন। এসপ্ল্যানেডে বা হাইকোর্টের ওদিকে গিয়ে ট্রাম ধরবেন। সুলতা এবং সুরেশ্বর ছাড়া মাত্র জন পাঁচ ছয় লোক ছিল। তার মধ্যে দুতিনজন হাউসের কর্মচারী।
তার মুখের দিকে তাকিয়ে সুলতার মনে হচ্ছিল—এ যেন আর একজন—সে নয়। সে ছিল উল্লসিত উদ্ভাসিত বেপরোয়া একজন। এ যেন ক্লান্ত প্রশান্ত মানুষ একজন। সুরেশ্বর
বললে—চল!
—আজ? তুমি পাগল?
—সে তো চিরকালের। পাগলামি আমার আছে সেটা জানি বলেই উন্মাদ নই। তবে যে-কোন মুহূর্তে পাগল হতে পারি। উঠতে পারে পাগলামি। বলেই সে খপ করে তার হাত ধ’রে বললে-চল!
চমকে উঠল সুলতা। কিন্তু রুষ্ট হতে পারলে না। কারণ এ হাত ধরা জোর করে হাত ধরা নয়, এ হাত ধরার মধ্যে মিনতি অত্যন্ত স্পষ্ট।
সে বললে—ছাড়।
ছেড়ে দিলে হাত সুরেশ্বর। বললে—জোর নেই তোমার ওপর। কিন্তু গেলে আমি খুশী হতাম। ছবি দেখে কে কি বুঝবে জানিনে। বোঝাবার গরজও নেই আমার। ছবির ভেতর জবানবন্দী—ছবির রঙে হারিয়ে যাবার ভয় আছে। তাতে শিল্পী সুরেশ্বর জিতবে। কিন্তু মানুষ সুরেশ্বর বোবা আসামীই থেকে যাবে। তোমাকে পেলে তোমার কাছে সে বাঙ্ময় হতে পারত। বাচালও হয়তো হতো। এখানে যে নাটকের যবনিকাপাতের জন্য উল্লাস করছ সেখানে গেলে নাটকটার ম্যানাস্ক্রিপটা দেখতে পেতে। আচ্ছা—
বসে সে দীর্ঘ পদক্ষেপে এগিয়ে গেল ফটকের দিকে।
সুলতার ভুরু দুটি কুঁচকে উঠল। মনের মধ্যে যেন দ্বিধা জেগেছে একটা। ওই লোকটার সম্পর্কে ধারণা তার যত খারাপ হোক তবু কি জানি কেন যেন একটা করুণা জাগছে। হাতের ঘড়িটার দিকে একবার সে চেয়ে দেখলে। নটা বেজে চার মিনিট। জানবাজার কাছেই। একবার ওর ওখান হয়ে গেলে কি হয়? বড়জোর দশটা, সওয়া দশটাই বাজবে। তাতে খুব দেরী হবে না। সে ডাকলে—দাঁড়াও। শুনছ!
সুরেশ্বর তখন ফটকে। সে ফিরে দাঁড়াল।
—কিছু বলছ?
—হ্যাঁ। কাছে এসে বললে-চল, কিন্তু আধঘণ্টার বেশী না।
—তা হলে একটা ট্যাক্সি নিই।
—সেই ভাল।
একটু এগিয়ে এসে রাজভবনের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণটায় কয়েক মিনিট দাঁড়াতেই ট্যাক্সি একটা মিলল, তাতে চড়ে বসে এসে সেই জানবাজারের বাড়ীর সামনে দাঁড়াল। বাড়ীটা চেনা যায় না। দীর্ঘদিন এ পথে সুলতা হাঁটেনি। সর্বাগ্রে চোখে পড়ে তার একটা আধুনিক বহিসজ্জা। রেলিং-দেওয়া জোড়া জোড়া গোল থামওয়ালা সেই একশো সওয়াশো ফুট লম্বা বারান্দাটা বন্ধ করে আধুনিক প্যাটার্নের একটা চেহারা দেওয়া হয়েছে।
সুলতা দাঁড়িয়ে দেখলে বাড়ীটাকে। তারপর বললে—এটা কি করেছ বল তো?
—বারান্দাটাকে ঘেরার কথা বলছ?
—হ্যাঁ। হঠাৎ হেসে বললে—তবে তোমার মনটা ফুটে উঠেছে। তুমি ফুটে উঠেছ এর মধ্যে।
হাসলে সুরেশ্বর, বললে—বলতে পার। তবে কি জান, এসব কথা আমার গা-সওয়া হয়ে গেছে। প্রথম যখন দাড়ি গোঁফ চুল রেখে আলখাল্লা পরতাম তখন শুনেছি। এখনও শুনি। আর অল্পবিস্তর সকলের চেহারাই তো এই। সে রাজার ছেলে গৌতম সিদ্ধার্থের চাঁচর চুল কেটে চীরবস্ত্র পরে বনে যখন তপস্যায় গেলেন তখন দেবদত্তরা এই ধরণের কথা বললে তো মিথ্যে বলে নি। অন্ততঃ প্রথম প্রথম যে দেখেছে সেই বলেছে—মানায় নি। ব্যারিস্টার গান্ধী যখন প্রথম গান্ধীর সাজ পরেছিলেন তখনও কি এমন ভাবে নি লোকে? তারপর ধর তোমার কথা। তোমাকে যেদিন প্রথম দেখি সেদিন ঠোঁটে তোমার লিপস্টিক ছিল, মনে পড়ছে আমি একটু বাঁকা কথা বলেছিলাম। আজ তুমি এমনই সেজেছ বা হয়েছ যে সেই লিপস্টিকের কথা তুললে এই ধরণেরই কথা হবে।
সুলতা তার মুখের দিকে তাকালে। ভুরু তার কুঁচকে উঠেছিল। কিন্তু সুরেশ্বরের মুখ সেই তেমনি বিষণ্ণ প্রশান্ত হয়ে আছে। যুদ্ধ করার বা ঝগড়া করার মনের কোন প্রকাশ ফুটে ওঠেনি সেখানে। কণ্ঠস্বরেও উত্তাপ নেই।
সুরেশ্বর বুঝেছিল, সে হেসে বললেনা, ঝগড়া আমি করিনি। বলছি কি জান, বলছি পরিবর্তন কালের নিয়ম। সেটা যেমন মানুষের হয় তেমনি মানুষের বিচরণক্ষেত্রে সর্বত্রই হয়। পুরনো বাড়ীতে নোনা ধরে। ফাট ধরে। তখন ভেঙে চুরে মেরামত করতে হয়। আবারও বংশও বাড়ে। তখন পাঁচিল ওঠে। জানালা ফুটিয়ে দরজা করতে হয়। বারান্দা ঘিরে ঘর বাড়াতে হয়।
সবিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে সুলতা বললে—বিয়ে করেছ? ছেলেপিলে বুঝি অনেকগুলো হয়েছে এর মধ্যে? মুখে হাসি এবং দৃষ্টিতে কৌতুক ফুটিয়ে সুলতা তার দিকে তাকালে।
সুরেশ্বর বললে—দেখো, প্রথমটা স্থির করেছিলাম বাড়ীটায় দুর্ভাগিনী মেয়েদের জন্যে একটা হোম-টোম বা আশ্রম-টাশ্রম করব। তখনই এই বারান্দা ঘেরার ব্যবস্থা হয়।
—সেই শেফালি কেমন আছে? যাকে করুণা করতে আমিই বলেছিলাম। তারপর তা থেকেই বুঝি তোমার করুণার স্রোত একেবারে ঝরঝর করে ঝরল—যার তোড়ে ঐরাবত ভেসে গেল!
—জানিনে ঠিক। তার খবর আর রাখিনি। ছেড়ে দাও ওকথা। তারপর মত বদলে ভেবেছিলাম অনাথ আশ্রম করব। বারান্দাটায় ক্লাস বসবে। কিন্তু তাও হয়নি। বারান্দা ঘেরার ইতিহাসটা এই, তবে ওর মধ্যে যেটা আধুনিক মেট্রো প্যাটার্ন চাপানো হয়েছে সেটা নেহাতই ইঞ্জিনিয়ার আর রাজমিস্ত্রীর কেরামতি। এখন ভিতরে এস। বাইরে ঝলমলে আলো পড়েছে, তার মধ্যে আমরা দুজনে পথে দাঁড়িয়ে বাগবিস্তার করছি, এতে জনসাধারণ কৌতূহলী হয়ে উঠেছে।
কথাটা ঠিক। রাস্তার সামনের দোকানে বেশ জটলা জমেছে। রাণী রাসমণির বাড়ীর নিচে বাইরের দিকটায় অসংখ্য দোকান। মশলাপাতি বিশেষ করে সুপুরীর পাইকারি দোকান অজস্র। তারই মধ্যে ছোট্ট তেলেভাজার দোকান থেকে নানান দোকান রয়েছে। দোকান-আইন মেনেও তার ঝাঁপ আধখানা বন্ধ করে হিসেব-নিকেশ মেলাচ্ছে, মধ্যে মধ্যে কৌতূহলী হয়ে তাদের দিকেই তাকাচ্ছে। ফ্রি স্কুল স্ট্রীট থেকে মোড় ফিরে ফিরিঙ্গী মেয়েরা যাচ্ছে, কেউ হেঁটে কেউ রিকশায়, পিছনে তাকাচ্ছে শিকার অদৃশ্য সুতোয় গাঁথা মাছের মত পিছনে আসছে কিনা? অ্যাংলো ইন্ডিয়ান এবং হাওয়াই শার্ট প্যান্ট পরা দেশী বাবুসাহেবরাও যাচ্ছে। সকলেই ওই আলোঝলমল স্থানটায় এসে সবিস্ময়ে তাকাচ্ছে। বাড়ীটা প্রায় বারো মাস অন্ধকার থাকে—হঠাৎ সেটার হল কি যে এমন আলোর জৌলুস ফুটিয়ে রঙ্গমঞ্চে পাদপ্রদীপের সামনে প্রধানা অভিনেত্রীর মত কোনও এক বিশেষ রজনী উপলক্ষে রাজরাণীর পোশাকে মুখে পেন্ট মেখে দাঁড়াল? তারপরই চোখ পড়েছে ওদের দুজনের দিকে।
সুলতা বললে—চল।
ভিতরে এসে ওই বারান্দাঘেরা হলটায় নিয়ে এল তাকে সুরেশ্বর। এবং যে আলোগুলো নিভানো ছিল তাও জ্বেলে দিলে। ঘরখানা ঝলমল করে উঠল শুধু আলোর নয় ছবির রঙের উপর পড়া আলোর প্রতিচ্ছটাতেও বটে। রঙের আভাও ফুটে উঠল আলোর সঙ্গে।
সবিস্ময় দৃষ্টিতে সে তাকালে ছবিগুলোর দিকে। মুগ্ধবিস্ময়ে দেখছিল। এত ছবি! এত ছবি এঁকেছে সে এই এতদিন অজ্ঞাতবাসে আত্মগোপন করে? ফিরে সে তাকালে সুরেশ্বরের দিকে। তারপর বললে—এত ছবি এঁকেছ?
—এর তিন-চার গুণ ছবি এঁকেছি! কিন্তু এখানে সব ধরবার কথা নয়। আর সেগুলো যা আমি বলতে চেয়েছি ছবির মধ্যে তার সঙ্গে হয়তো সম্পর্ক ক্ষীণ বা মাত্রা ছাড়িয়ে বলা হয় বলে টাঙাই নি।
ছবিগুলোর দিকে আবার তাকালে সুলতা। দেখতে দেখতেই বললে—ছবির মধ্যে কিছু বলতে চেয়েছ নাকি?
তাই জন্যেই তোমায় আমার আজ সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন ছিল দেখাবার। এবং সর্বাগ্রে দেখবার এ তো ছবির প্রদর্শনী নয়, কীর্তিহাটের কড়চা—সুরেশ্বরের জবানবন্দী। ছবি থেকে যাঁরা বুঝতে পারবেন তাদের নমস্কার। তাঁরা রসিক এবং রসিকের চেয়েও বেশী কিছু। কিন্তু কি বলতে চেয়েছি তা যাদের কাছে বলতে পারি তার মধ্যে তুমি প্রথম এবং প্রধান।
হাসলে সুলতা। মনে মনে বলতে গিয়ে মুখে বেরিয়ে এল কথাটা। বললে—বড্ড দেরী হয়ে গেছে সুরেশ্বর। আমি অনেক দূরে বাস করি। নিউ আলিপুরে।
—তা জানি। তবে একটা কথা বলি। আজ নানান জমিদারের বাড়ীতে আসর পড়েছে। আমার মনে হচ্ছে বর্ধমানের মহারাজা সম্ভবত গোলাপবাগের প্রাসাদ থেকে প্যালেস পর্যন্ত ঘুরছেন ছবি দেখে দেখে। মন চলে গেছে ১৭৯৯ পার হয়ে ১৭৫৭-তে। তা পার হয়ে আরও পিছনে, শোভা সিং যখন কৃষ্ণকুমারীর ছুরিতে মরেছিলেন সে আমলে। ওঁকে দেখছি, ইমোশনাল লোক। হয়তো ভাবছেন ডিনামাইট দিয়ে এই রাত্রেই সব চুরমার করে দেবেন। তারপর হয়তো ভাবছেন, না, সব তিনি গভর্নমেন্টকে দান করে দেবেন। কুমার বিমলচন্দ্র সিংহ হয়তো দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের ছবির তলায় দাঁড়িয়ে মুচকে মুচকে হাসছেন। বলছেন—তোমার প্রবর্তন করা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত যারা আজ নাকচ করলে তাদের মধ্যে আমিও একজন। কোন জমিদার হয়তো একা বসে কাগজের উপর হিসেব করে দেখছেন কম্পেনশেসন কত পাবেন। কেউ কেউ গাল দিচ্ছেন যারা এটা করলে তাদের। এমন লোকও হয়তো এক-আধজন আছেন যাঁরা প্রচুর পরিমাণে মদ্য পান করছেন। কেউ যদি বাঈজী বাড়ী গিয়ে শেষ উৎসব করেন তবে তাঁকে আমার সেলাম রইল। আমি এই ছবির আসর পেতেছি। ভেবেছিলাম সারা রাত একলাই এপাশ থেকে ওপাশে ঘুরব! ভাগ্যক্রমে এমন জনকে পেলাম যাকে আমি চেয়েছি মনে মনে ছবিগুলো আঁকবার সময় থেকে টাঙাবার সময় পর্যন্ত।
হঠাৎ একটা লম্বা ছবি, যেটা টেবিলের উপর রাখা ছিল সেটা তুলে নিয়ে প্রথম ছবিটার ফ্রেমে ঠেকিয়ে বললে—এই আমার প্রথম ছবি সুলতা। কংসাবতীবারি-বিধৌত তট—বনচ্ছায়া- শীতল কীর্তিহাট নামক গ্রাম। ১৮০১ সাল!
প্রকাণ্ড বড় বড় ছবি। অয়েলে আঁকা। চার ফুট তিন ফুট বা তার চেয়েও বড়। সুন্দর ছবি। যেমন বর্ণাঢ্য তেমনি বিচিত্র টেকনিকে আঁকা। যেমন আমাদের দেশের মন্দিরের ভিতর দিকে পোড়ামাটির কাজের মধ্যে কৃষ্ণলীলা রামলীলা ফোটানো হয় তেমনি ঢঙে আঁকা। গ্রাম নদী বন সব আছে পটভূমিতে। গ্রামের খড়ের চাল ঘরের চালগুলিতে সোনালী হলুদ রঙ চমৎকার লাগছিল, তারই মধ্যে সাদা একখানা পাকা বাড়ী। এও পটভূমির কোলে দ্বিতীয় পটভূমি। ছবিটার কেন্দ্র-বিন্দু পথ—পথের উপর পাল্কি চলছে। তার মধ্যে টোপর মাথায় মুকুট মাথায় বালক-বালিকা বর-কনে। বরের হাতে একখানা কাগজ
তার পিছনে নরনারী। বাদ্যভাণ্ড। আসাসোঁটা হাতে বরকন্দাজ পাইক।
দেখছিল সুলতা।
সুরেশ্বর বললে-রায়বংশের প্রথম জমিদার সোমেশ্বর রায় ১৮০১ সালে দশ বৎসর বয়সে জমিদার হয়েছিলেন। বিয়ে করে তিনি গ্রামে প্রবেশ করছেন।
হঠাৎ সে উঠে দাঁড়াল, বললে-ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ!
চকিত হয়ে উঠল সুলতা। ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ?
সুরেশ্বর সেই মুহূর্তেই বললে—না, আমার ভুল হয়েছে। এখানে তো তুমি একা রয়েছ সুলতা! আর তো কেউ নেই!
তারপর হেসে বললে—আমার হঠাৎ মনে হয় ঘরখানা নরনারীতে ভরে গেছে! এমন ভুল আমার হয় মধ্যে মধ্যে। একটু আগে বলছিলাম, তুমিও জান, একটা পাগলামি আমাদের বংশে আছে। প্রথমে খেয়াল বলে চলে যায়, কিন্তু খেয়াল যতক্ষণ মাত্রা না ছাড়ায়। মাত্রা ছাড়ালেই হয় পাগলামি। আমার মাত্রা অনেক দিন ছাড়িয়েছে। তারপর কীর্তিহাটে গিয়ে সেটা আমার মন বুদ্ধি আমার বাসনা কামনাকে এমনভাবে অভিভূত করলে যে আমার সব বেঠিক হয়ে গেল। তার উপর প্রচুর মদ্যপান করতাম। সেটা তাকে বাড়িয়ে তুলত। আমি কল্পনায় নানান ছবি, নানা মানুষ দেখি অন্ধকার রাত্রে। দিনে দেওয়ালের গায়ে ছাদে চটে-যাওয়া পলেস্তারার মধ্যে দেখতে পাই নানান ছবি, নানান মানুষ। কখনও কখনও জীবন্ত হয়ে তারা কথা বলে। আজও আমার হঠাৎ মনে হল ছবির মানুষগুলো ছবি থেকে নেমে এসে ঘর ভরে বসেছে! এরা যে ঐতিহাসিক সুলতা, কাল্পনিক তো নয়। এদের অশরীরী আত্মা এসে বসেছে মনে হল। তারাও দেখতে এসেছে ছবিতে ‘কীর্তিহাটের কড়চা’। শুনতে এসেছে সুরেশ্বরের জবানবন্দী!
সুলতার মনে হল সুরেশ্বর যেন কত দূরে—অনেক দূরের দিকে চেয়ে রয়েছে।