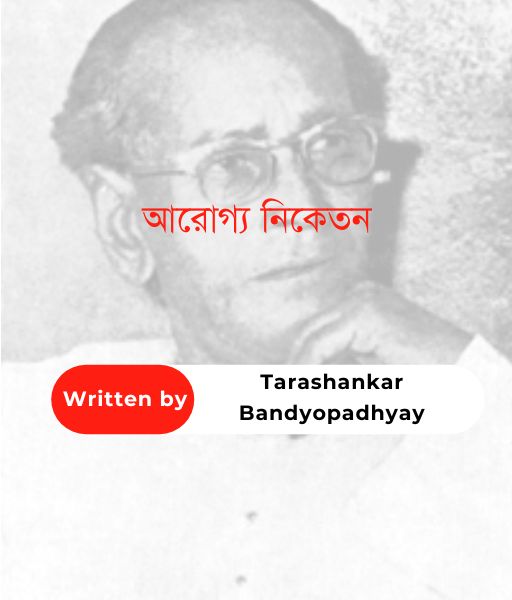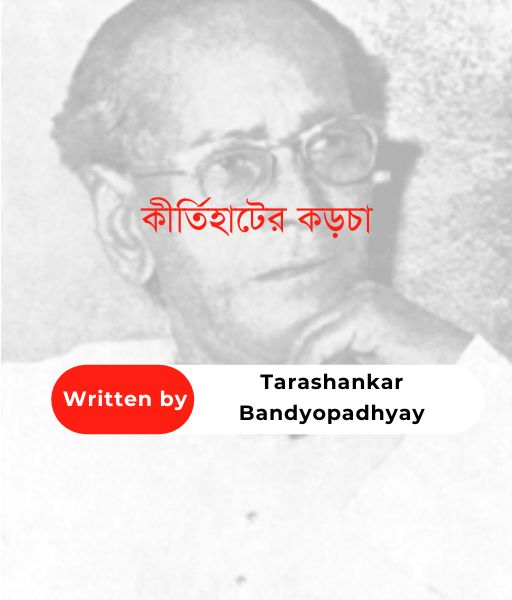নদীর ওপারে একটা চর
নদীর ওপারে একটা চর দেখা দিয়েছে।
রায়হাট গ্রামের প্রান্তেই ব্রাহ্মণী নদী–ব্রাহ্মণীর স্থানীয় নাম কালিন্দী, লোকে বলে কালী নদী; এই কালী নদীর ওপারে চর জাগিয়াছে। এখন যেখানে চর উঠিয়াছে পূর্বে ওইখানেই ছিল কালী নদীর গর্ভভূমি। এখন কালী রায়হাটের একাংশ গ্রাস করিয়া গ্রামের কোলে কোলে বহিয়া চলিয়াছে। গ্রামের লোককে এখন বিশ হাত উঁচু ভাঙন ভাঙ্গিয়া নদীগর্ভে নামিতে হয়।
ওই চরটা লইয়া বিবাদ বাধিয়া উঠিল। রায়হাট প্রাচীন গ্রাম। এখানকার প্রাচীন জমিদার-বংশ রায়েরা শাখা-প্রশাখায় বহুধা বিভক্ত। এই বহুবিভক্ত রায়-বংশের প্রায় সকল শরিকই চরটার স্বামীত্ব লাভ করিবার নিমিত্ত এক হাতে লাঠি ও অপর হাতে কাগজ লইয়া অগ্রসর হইলেন। ইঁহাদের মধ্যে আবার মাথা গলাইয়া আসিয়া প্রবেশ করিল জন দুয়েক মহাজন এবং জন কয়েক চাষীপ্রজা। সমস্ত লইয়া বিবদমান পক্ষের সংখ্যা এক শত পনেরোয় গিয়া দাঁড়াইয়াছে, প্রত্যেকেই প্রত্যেকের বিরোধী। জমিদারগণের প্রত্যেকের দাবি–চর তাহার সীমানায় উঠিয়াছে, সুতরাং সেটা তাহারই খাস-দখলে প্রাপ্য। মহাজন দুইজনের প্রত্যেকের দাবি, তাহার নিকট আবদ্ধীয় জমির সংলগ্ন হইয়া উঠিয়াছে, সুতরাং চর তাঁহার নিকট আবদ্ধীয় সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হওয়া উচিত এবং নাকি তাহাই হইতে হইবে। প্রজা কয়েক জনের দাবি–কালীর গ্রাসে এপারে তাহাদের জমি গিয়াছে, সুতরাং ওপারে যে ক্ষতিপূরণ কালী দিয়াছে সে প্রাপ্য তাহাদের।
রায়-বংশের বর্তমানে এক শত পাঁচ জন শরিক, বাকী খাজনার মকদ্দমায় জমিদারপক্ষীয় গণের নাম লিখিতে, তিন পৃষ্ঠা কাগজ পূর্ণ হইয়া যায়। ইহাদের মধ্যে যোগ দিয়াছেন এক শত দুই জন। বাকী তিন পক্ষের মধ্যে এক পক্ষের মালিক নিতান্তই সঙ্গতিহীন নাবালক। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পক্ষ কিন্তু এখানকার বহুকালের দুইটি বিবদমান পক্ষ। এক পক্ষ রায়-বংশের দৌহিত্র বংশ, অপর পক্ষ রায়-বংশেরই সর্বাপেক্ষা ধুরন্ধর ব্যক্তি কূট-কৌশলী ইন্দ্র রায়। ইন্দ্র রায়ের হাত গরুড়ের তীক্ষ্ণ নখরের মত প্রসারিত হইলে কখনও শূন্য মুষ্টিতে ফেরে না, ভূখণ্ডও বোধ করি উপড়াইয়া উঠিয়া আসে। এই ইন্দ্র রায়ের অপেক্ষাতেই বিবদমান পক্ষ সকলেরই উদ্যত হস্ত এখনও স্তব্ধ হইয়া আছে, অন্যথায় এতদিন একটা বিপর্যয় ঘটিয়া যাইত।
অপর পক্ষ–ইন্দ্র রায়ের বংশানুক্রমিক প্রতিপক্ষ রামেশ্বর চক্রবর্তী। তিনিও এক কালে ইন্দ্র রায়ের সমকক্ষ ব্যক্তি ছিলেন; কূট বুদ্ধি অপেক্ষা ব্যক্তিত্ব ছিল তাহার বড়; দাম্ভিকতার প্রতিমূর্তি। ইন্দ্র রায়ের সহিত দ্বন্দ্বে ইন্দ্র রায়কেই অস্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করিতেন; প্রতি ক্ষেত্রে তিনি সাক্ষী মানিতেন ইন্দ্র রায়কে। ইন্দ্র রায় মিথ্যা বলিলে তিনি হাসিয়া তাহার দাবি প্রত্যাহার করিয়া বলিতেন, তোমার সাক্ষী দেওয়ার ফী দিলাম ইন্দ্র। মিছেই খরচ করে সাক্ষীদের তুমি জুতো কিনে দিলে। বাড়ি ফিরিয়া তিনি গ্রামে বড় একটা খাওয়া-দাওয়া জুড়িয়া দিতেন।
কিন্তু যে কালের গতিতে যদুপতি যান, তাহার মথুরাপুরীও গৌরব হারায়, সেই কালের প্রভাবেই বোধ করি সে রামেশ্বর আজ আর নাই। তিনি নাকি দৃষ্টিহীন হইয়া অন্ধকার ঘরে বিছানায় পড়িয়া আছেন ভূমিশায়ী জীর্ণ জয়স্তম্ভের মত। চোখে নাকি আলো একেবারে সহ্য হয় না, আর মস্তিষ্কও নাকি বিকৃত হইয়া গিয়াছে। সম্পত্তি পরিচালনা করে প্রাচীন নায়েব যোগেশ মজুমদার; যোগেশ মজুমদারের অন্তরালে আছেন শান্ত বিষাদপ্রতিমার মত একটি নারীমূর্তি রামেশ্বরের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী সুনীতি দেবী। দুইটি পুত্র-বড়টির বয়স আঠারো, ছোটটি সবে পনেরোয় পা দিয়াছে; সম্প্রতি মজুমদার সুনীতি দেবীকে অনেক বলিয়া কহিয়া বড়টিকে পড়া ছাড়াইয়া বিষয়কর্মে লিপ্ত করিয়াছেন। অবশ্য লেখাপড়াতেও তাহার অনুরাগ বলিয়া কিছু ছিল না। এই বিবাদ আরম্ভ হইবার পূর্ব হইতেই মজুমদার এবং রামেশ্বরের জ্যেষ্ঠ পুত্র মহীন্দ্র এখানে নাই–তাহারা দূর মহালে গিয়াছে মহাল পরিদর্শনে। লোকে বুঝিল, হয় ইন্দ্র রায় প্রতিদ্বন্দ্বীর অপেক্ষায় আছেন, নয় সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছেন, উপযুক্ত সময়ে ছোঁ মারিয়া বসিবেন।
চাষী প্রজারা এতটা বোঝে নাই, তাহারা সেদিন আসিয়া ইন্দ্র রায়কেই ধরিয়া বসিল, হুজুর, আপনি একটা বিচার করে দ্যান।
অতি মৃদু হাস্যের সহিত অল্প একটু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তিনি বলিলেন, কিসের রে?–যেন তিনি কিছুই জানেন না–কার সঙ্গে ঝগড়া হল তোদের?
উৎসাহিত হইয়া প্রজারা বলিল, আজ্ঞে, ওই লদীর উ-পারের চরটার কথা বলছি। ই-পারে আমাদের জমি খেয়ে তবে তো লদী উ-পারে উগরেছে; আমাদের জমি যে পয়োস্তি হল– তার খাজনা তো আমরা কমি পাই নাই, আমরা তো বছর বছর লোকসান গুনে যাচ্ছি।
বাঁ হাতে গোঁফে তা দিতে দিতে রায় বলিলেন, বেশ তো, লোকসান দিয়ে দরকার কি তোদের? লোকসানী জমা ইস্তফা দিলেই পারিস। বাঁ হাতে গোঁফে তা দেওয়া রায়ের একটা অভ্যাস। লোক বলে, ওই সঙ্গে তিনি মনে মনে বুদ্ধিতে পাক মারেন।
প্রজারা হতভম্বের মত রায়ের মুখের দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিল, আজ্ঞে, ই তা হলে বিচার কি করলেন আপনি?
হাসিয়া ইন্দ্র রায় বলিলেন, তোরা যা বলবি, তাতে সায় দেওয়ার নামই তো বিচার নয় রে! বিচারের তো একটা আইন আছে, সেই আইনমতেই তো জজকে রায় দিতে হয়।
প্রজারা হতাশ হইয়া উঠিয়া চলিয়া গেল। যাইবার পথে তাহারা পরামর্শ করিয়া উঠিল গিয়া রামেশ্বরবাবুর বাড়ি। কাছারিতে মালিক কেহ নাই, চাকরটা বলিল, বড়বাবুও নাই, নায়েববাবুও নাই, কর্তাবাবুর সঙ্গে তো দেখা হবেই না।
প্রজারা গ্রামেরই লোক, তাহারা সকল সংবাদই রাখে, তাহারা জানে, এখন এ বাড়ির সব কর্মের অন্তরালে একটি দৃশ্য শক্তি কাজ করে, পরমাশক্তির মত তিনিও নারীরূপিণী। তাহারা বলিল, আমরা মায়ের সঙ্গে দেখা করব।
চাকরটা অবাক হইয়া গেল, এমন ধারার কথা সে কখনও শোনে নাই। সে বলিল, তোমরা কি ক্ষেপেছ নাকি?
রামেশ্বরবাবুর ছোট ছেলে অহীন্দ্র পাশেই একখানা ঘরে পড়িতেছিল, সে এবার বাহির হইয়া আসিল। খাপখোলা তলোয়ারের মত রূপ–ঈষৎ দীর্ঘ পাতলা দেহ, উগ্রগৌর দেহবর্ণ, পিঙ্গল চোখ, মাথার চুল পর্যন্ত পিঙ্গলাভ। তাহাকে দেখিয়া প্রজারা উৎসাহিত হইয়া উঠিল। এ-বাড়ির বড় ছেলে মহীন্দ্রকে দেখিয়া তাহাদের ভয় হয়, দশটা কথার পর মহীন্দ্র একটা জবাব দেয়, তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়া পর্যন্ত সে কখনও কথা বলে না। আর এই ছোটদাদা বাবুটির রূপ যতই উগ্র হউক না কেন, এমন নিঃসঙ্কোচ স্বচ্ছন্দ ব্যবহার, এমন মধুমাখা মিষ্ট কথা তাহারা কাহারও কাছে পায় না। গল্প লইয়া তাহাদের সহিত তাহার মিলনক্ষেত্র গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রাচীন চাষীদের কাছে সাঁওতাল বিদ্রোহের গল্প শুনিতে যায়, সে নিজে বলে দেশবিদেশের কত গল্প। সমুদ্রের ধারে সোমনাথ শিবমন্দির লুঠের কথা, আমেরিকার সাহেবদের সঙ্গে বিলেতের সাহেবদের লড়াইয়ের কথা। তাহারা বিস্ময়বিমুগ্ধ হইয়া শোনে। অহীন্দ্রকে দেখিয়া তাহারা পরম উৎসাহের সহিত বলিল, ছোটদাদাবাবু কবে এলেন?
অহীন্দ্র এখান হইতে দশ মাইল দূরে শহরের স্কুলে পড়ে। অহীন্দ্র হাসিয়া বলিল, কাল সন্ধ্যাবেলা এসেছি, চারদিন ছুটি আছে। তারপর, তোমরা এসেছ কোথায়? দাদাও বাড়ি নেই, নায়েব-কাকাও নেই।
তাহারা বলিল, আপনি তো আছেন দাদাবাবু, আপনি আমাদের বিচার করে দ্যান।
খিলখিল করিয়া হাসিয়া অহীন্দ্র বলিল, আমি বিচার করতে পারি নাকি, দূর দূর!
তাহারা ধরিয়া বসিল, না দাদাবাবু, আপনাকে আমাদের এ দুঃখের কথা শুনতেই হবে। না শুনলে আমরা দাঁড়াব কার কাছে? নইলে নিয়ে চলুন আমাদের মায়ের দরবারে। আমরা না খেয়ে পড়ে থাকব এইখানে।
অহীন্দ্র মায়ের কাছে গেল। সুনীতি স্বামীর জন্য আহার প্রস্তুত করিতেছিলেন। অহীন্দ্র আসিয়া দাঁড়াইতে বলিলেন, কি রে অহি?
মা ও ছেলের এক রূপ, তফাৎ শুধু চুল ও চোখের। মুখ, রং ও দেহের গঠনে অহি যেন মায়ের প্রতিবিম্ব–কেবল পিঙ্গল চুল ও চোখ তাহার পিতৃবংশের বৈশিষ্ট্য। সুনীতির বড় বড় কালো চোখ, চুলও ঘন কৃষ্ণবর্ণ। তাহার বড় ছেলে মহীর সহিত তাহার কোন সাদৃশ্যই নাই, সর্ব অবয়বে সে তাহার পিতার অনুরূপ।
অহি সকল কষা মাকে বলিয়া বলিল, ওরা একবার তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে মা। কি বলব ওদের? ছেলের মুখের দিকে চাহিয়া মা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, সে কখনও হয় অহি? আমি কেন দেখা করব ওদের সঙ্গে? তুই একথা বলতে এলি কি বলে?
অহি সঙ্গে সঙ্গে ফিরিল। মা হাসিয়া পিছন হইতে ডাকিয়া বলিলেন, অমনি চললি যে?
অহি পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, বলি গে ওদের সেই কথা।
কই, একবার মুখখানা দেখি।
ছেলে ফিরিয়া দাঁড়াইল, মা তাহার চিবুকখানা স্পর্শ কৱিয়া বলিলেন, এমন ফুলটুস ছেলে আমি কোথাও দেখি নি। একেবারে ফুলের ঘায়েও রাগ হয়ে যায়।
সত্য কথা, মায়ের সামান্য কথাতেই অহির অভিমান হইয়া যায়। এ সংসারে তাহার সকল আবদার একমাত্র মায়ের উপর। শৈশব হইতেই সে বাপের কাছে বড় ঘেঁষে না, তাহার বড় ভাই মহীন্দ্র বরং পিতার কাছে কাছে ফিরিয়া থাকে। দুই ভাই প্রকৃতিতে যেন বিপরীত। মহীন্দ্র অভিমান জানে না, সে জানে দুর্দান্ত ক্রোধে আত্মহারা হইয়া আঘাত করিতে, শক্তিবলে আপনার ঈপ্সিত বস্তু মানুষের কাছ হইতে আদায় করিয়া লইতে। ইস্পাতের মত সে ভাঙিয়া পড়ে, তবু কোনমতেই নত হয় না। আর অহি খাঁটি সোনার মত নমনীয়–আঘাতে ভাঙে না অভিমানে বাঁকিয়া যায়।
মা আবার প্রশ্ন করিলেন, রাগ হল তো অমনি?
না।
কেন? আমি যে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। তুই বুঝি ওদের বলেছিস, মায়ের সঙ্গে দেখা করিয়ে দিবি?
অহি বলিল, বলি নি, কিন্তু দেখা করতে ক্ষতি কি?
ক্ষতি নেই, বলিস কি তুই? রায়-বাবুরা যে হাসবে, বলবে, বাড়ির বউ হয়ে চাষা প্রজাদের সঙ্গে কথা কইলে!
বলুক গে। তাই বলে ওরা ওদের দুঃখের কথা বলতে এলে শুনবে না? আর, এমনধারা মুসলমান নবাববাড়ির মত পর্দার দরকারই বা কি? আজকাল মেয়েরা দেশের কাজ করছে! ইউরোপে–এই যুদ্ধে–
বাধা দিয়া মা হাসিয়া বলিলেন, তোর মাস্টারিতে আর আমি পারি নে অহি। তা তুই নিজে শুনে যা বলতে হয় বল না; সেইটেই আমার বলা হবে। আমি মহীকে বলব, আমিই বলেছি এ কথা।
ছেলে জেদ ধরিল, না, সে হবে না, তোমাকেই শুনতে হবে। আমি বরং দরজায় দাঁড়িয়ে থাকব। ওরা বাইরে থাকবে, তুমি ঘরে থাকবে।
শেষে তাহাই হইল। অহীন্দ্রকে মধ্যে রাখিয়া সুনীতি প্রজাদের অভিযোগ শুনিতে বসিলেন। তাহারা আপনাদের যুক্তিমত দাবি জানাইয়া সমস্ত নিবেদন করিল, প্রকাশ করিল না শুধু ইন্দ্র রায়ের নিকট শরণ লইতে যাওয়ার কথা এবং রায়-মহাশয়ের সুকৌশল প্রত্যাখ্যানের কথা। তাহারা বক্তব্য শেষ করিয়া বলিল, আপনার চরণে আমরা আশ্রয় নিলাম মা, আপনি ইয়ের ধর্মবিচার করে দ্যান। কালীর গেরাসে আমাদের সবই গিয়াছে মা, আমাদের আলু লাগাবার জমি নাই, আখ লাগাবার জায়গা নাই, আর কি বলব মা,–চাষীর বাড়িতে ছোলার ঝড় ওঠে না গম ওঠে না। আমরা তবু তো কখনও খাজনা না-দেওয়া হই নাই।
সুনীতি বলিলেন, তোমরা বরং ও-বাড়ির দাদার কাছে যাও। অহিকে তোমাদের সঙ্গে দিচ্ছি। ও-বাড়ির দাদা অর্থে ইন্দ্র রায় মহাশয়। প্রজারা ইন্দ্র রায়ের নাম শুনিয়া নীরব হইয়া গেল। রংলাল চট করিয়া বুদ্ধি করিয়া বলিল, আজ্ঞে না মা, উনি জমিদার বটেন; কিন্তু বুদ্ধিতে উনি জেলাপির পাক। যা করতে হয় আপুনি করে দ্যান।
সুনীতি বলিলেন, ছি বাবা, এমন কথা কি বলতে হয়। তিনিই হলেন এখন গ্রামের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। এ বাড়ির মালিকের অসুখের কথা তোমরা তো জান! মহী হাজার হলেও ছেলেমানুষ। আমি স্ত্রীলোক। সমস্ত গ্রামের জমিদার নিয়ে যে বিবাদ, তার মীমাংসা কি আমার দ্বারা হয় বাবা? যদি কখনও ভগবান মুখ তুলে চান, মহী অহি উপযুক্ত হয়, তবেই আবার তোমাদের অভাব-অভিযোগের বিচার এবাড়িতে হতে পারবে। এখন তোমরা ও বাড়ির দাদার কাছেই যাও। অহি তোমাদের সঙ্গে যাচ্ছে।
প্রজাদের মধ্যে রংলালই আবার বলিল, আজ্ঞে মা, তিনিও খামচ তুলেছেন। সেই তো আমাদের ভয়, নইলে অন্য জমিদারের সঙ্গে লড়তে আমাদের সাহস আছে। না হয় দশ টাকা খরচ হবে।
সুনীতি বলিলেন, তিনিও কি চরটা দাবি করেছেন না কি?
মুখে বলেন নাই, কিন্তু ভঙ্গী সেই রকমই বটে। গাঁসুদ্ধ জমিদারই দাবি করেছে মা, আমরাও দাবি করছি, আবার মহাজনেরাও এসে জুটেছে। দাবি করেন নাই শুধু আপনারা। অথচ–
অথচ কি মোড়ল? ওতে কি আমাদেরও অংশ আছে?
বার বার হতাশার ভঙ্গীতে মাথা নাড়িয়া রংলাল বলিল, কি আর বলি মা? আর বলবই বা কাকে? আইনে তো বলছে, চর যে-গাঁয়ের লাগাড় হয়ে উঠবে, সেই গাঁয়ের মালিক পাবে। তা চরখানি তো রায়হাটের সঙ্গে লেগে নাই। লেগে আছে উ-পারের চক আফজলপুরের সঙ্গে। তা আফজলপুর তো আপনাদেরই ষোল আনা। আর ই-পারে হলেও তো তারও আপনারা তিন আনা চার গণ্ডার মালিক।
অন্য প্রজারা রংলালের কথায় চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল। মানুষ বৃদ্ধ হইলে ভীমরতি হয়, নহিলে দাবি জানাইতে আসিয়া এ কি বলিতেছে বুড়া। সুনীতি একটু আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, দেখ বাবা, তোমার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। তোমরা দাবি করছ চর তোমাদের প্রাপ্য, এপারে কালী নদীতে জমি তোমাদের গেছে, ওপারের চরে সেটা তোমাদের পেতে হবে। আবার–
মধ্যপথেই বাধা দিয়া লজ্জিতভাবে রংলাল বলিল, বলছি বৈকি মা, সেটা হল ধর্মবিচারের কথা। আপনি বলেন, ধৰ্ম অনুসারে আমাদের পাওনা বটে কি না?
সুনীতি নীরবেই কথাটা ভাবিতেছিলেন, পাওয়া উচিত বৈকি। দরিদ্র চাষী প্রজা– আহা-হা!
রংলাল আবার বলিল, আর আমি যা বলছি–ই হল আইনের কথা। আইন তো আর ধন্মের ধার ধারে না। উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপানোই হল আইনের কাজ।
সুনীতি ধীরভাবে চিন্তা করিয়া শেষে বলিলেন, আচ্ছা, আজই আমি মহীকে আর মজুমদার ঠাকুরপোকে আসতে চিঠি লিখে দিচ্ছি। তাঁরা এখানে আসুন। তারপর তোমরা এস। তবে একথা ঠিক, তোমাদের ওপর কোন অবিচার হবে না।
রংলাল আবার বলিল, শুধু যেন আইনই দেখবেন না মা, ধম্মপানেও একটুকুন তাকাবেন।
সুনীতি বলিলেন, ধর্মকে বাদ দিয়ে কি কিছু করা যায় বাবা? কোন ভয় নেই তোমাদের।
প্রজারা কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া চলিয়া গেল।
সুনীতি বলিলেন, তুই ওবেলা একবার ও-বাড়ির দাদার কাছে যাবি অহি।
.
০২.
সুনীতি রায়-বংশের ছোট বাড়ির মালিক ইন্দ্র রায়কে বলেন–দাদা। কিন্তু ইন্দ্র রায়ের সঙ্গে তাহার কোন সম্পর্ক নাই। ইন্দ্র রায় রামেশ্বর চক্রবর্তীর প্রথমা পত্নী রাধারাণীর সহোদর। চক্রবর্তী-বংশের সহিত রায়-বংশের বিরোধ আজ তিন পুরুষ ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে; রায় বংশের সকলেই চক্রবর্তীদের প্রতি বিরূপ, কিন্তু এই ছোট বাড়ির সহিতই বিরোধ যেন বেশী। তবুও আশ্চর্যের কথা, রামেশ্বর চক্রবর্তীর সহিত ছোট বাড়ির রায়-বংশের কন্যার বিবাহ হইয়াছিল।
তিন পুরুষ পূর্বে বিরোধের সূত্রপাত হইয়াছিল। রায়েরা শ্রোত্ৰিয় এবং চক্রবর্তী-বংশ কুলীন। সেকালে শ্রোত্রিয়গণ কন্যা সম্প্রদান করিতেন কুলীনের হাতে। রামেশ্বরের পিতামহ পরমেশ্বর রায়-বংশের মাঝের বাড়ির সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। বিবাহ করিয়াও তিনি শ্বশুর বর্তমানে কখনও স্থায়ীভাবে শ্বশুরালয়ে বাস করেন নাই। শ্বশুরের মৃত্যুর পর তিনি যেদিন এখানে আসিয়া মালিক হইয়া বসিলেন, রায়েদের সহিত তাহার বিবাদও বাধিল সেই দিনই। সেদিনও রায়েদের মুখপাত্র ছিলেন ওই ছোট বাড়িরই কর্তা– এই ইন্দ্র রায়ের পিতামহ রাজচন্দ্র রায়। সেদিন পরমেশ্বর চক্রবর্তীর শ্বশুরের অর্থাৎ রায়-বংশের মাঝের বাড়ির কর্তার শ্রাদ্ধবাসর। রাজচন্দ্র রায়ের উপরেই শ্রাদ্ধের সকল বন্দোবস্তের ভার ন্যস্ত ছিল। মজলিসে বসিয়া রাজচন্দ্র গড়গড়ার নল টানিয়া পরমেশ্বর চক্রবর্তীর হাতে তুলিয়া দিলেন। পরমেশ্বর নলটি না টানিয়াই রায়-বংশধরের হাতে সমর্পণ করিলেন। তার পর নিজের ঝুলি হইতে ছোট একটি হুঁকো ও কল্কে বাহির করিয়া একজন চাকরকে বলিলেন, কোন ব্রাহ্মণকে দে, জল সেজে এই কল্কেতে আগুন দিয়ে দিক। তিনি ছিলেন পরম তেজস্বী তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ।
রাজচন্দ্র সম্বন্ধে পরমেশ্বরের শ্যালক, তিনি বলিলেন, ভণ্ডামিটুকু খুব আছে কুলীনদের।
হাসিয়া পরমেশ্বর বলিলেন, গুণ্ডামির চেয়ে ভণ্ডামি অনেক ভাল রায় মশায়।
রাজচন্দ্র উত্তর দিলেন, গুণ্ডামির অর্জিত ভূ-সম্পত্তি কিন্তু বড়ই উপাদেয়।
কথাটি শুনিয়া রায়-বংশের সকলেই হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।
পরমেশ্বর কিন্তু ক্রুদ্ধ হইলেন না, তিনি সঙ্গে সঙ্গেই মৃদু-হাস্যের সহিত উত্তর দিলেন, শুধু ভূমি-সম্পত্তিই নয় রায় মশায়, গুণ্ডাদের কন্যাগুলিও রত্নস্বরূপা; যদিও দুষ্কুলাৎ।
এবার মজলিসে যে যেখানে ছিল, সকলেই হাসিয়া উঠিল; হাসিলেন না কেবল রায়েরা। ফলে গোলও বাধিল। শ্রাদ্ধ অন্তে ব্রাহ্মণ-ভোজনের সময় রায়েরা একজোট হইয়া বলিলেন, পরমেশ্বর চক্রবর্তী আমাদের সঙ্গে এক গড়গড়ায় তামাক না খেলে আমরাও অন্ন গ্রহণ করব না।
পরমেশ্বর আপনার ছোট হুঁকাটিতে তামাক টানিতে টানিতেই বলিলেন, তাতে চক্রবর্তী বংশের কোন পুরুষের অধোগতি হবে না। ব্রাহ্মণ-ভোজনের অভাবে অধোগতি হলে রায় বংশেরই হবে।
অতঃপর রায়দের মাথা হেঁট করিয়া খাইতে বসিতে হইল। কিন্তু উভয় বংশের মনোজগতের মধ্যবর্তী স্থলে বিরোধের একটি ক্ষুদ্র পরিখা খনিত হইল সেই দিন।
পরমেশ্বর ও রাজচন্দ্রের সময়ে বিরোধের যে পরিখা খনিত হইয়াছিল তাহা শুধু দুই বংশের মিলনের পক্ষে বাধা হইয়াই প্রবাহিত হইত, গ্রাস কিছুই করে নাই। কিন্তু পরমেশ্বরের পুত্র সোমেশ্বরের আমলে পরিখা হইল তটগ্রাসিনী তটিনী; সে তট ভাঙিয়া কালী নদীর মত সম্পত্তি গ্রাস করিতে শুরু করিল। মামলা-মকদ্দমার সৃষ্টি হইল। রাজচন্দ্রের পুত্র তেজচন্দ্ৰই প্রথমটা ঘায়েল হইয়া পড়িলেন। সোমেশ্বরের একটা সুবিধা ছিল, সমগ্র সম্পত্তির মালিক ছিলেন সোমেশ্বরের জননী। সোমেশ্বরের মাতামহ দলিল করিয়া সম্পত্তি দিয়া গিয়াছিলেন কন্যাকে, কাজেই সোমেশ্বরের দায়ে তাঁহার সম্পত্তি স্পর্শ করিবার অধিকার কাহারও ছিল না। এই সময়ে বীরভূমের ইতিহাস বিখ্যাত সাঁওতাল বিদ্রোহ হয়। সোমেশ্বর অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া সাঁওতালদের সহিত যোগ দিয়া বসিলেন। কপালে সিন্দুরের ফোঁটা আঁকিয়া তিনি নাকি সাঁওতাল-বাহিনী পরিচালনাও করিয়াছিলেন। এই লইয়া মাতা-পুত্রে বচসা হয়, পুত্র তখন বিদ্রোহের উন্মাদনায় উন্মত্ত। সে মাকে বলিয়া বসিল, তুমি বুঝবে না এর মূল্য, শ্রোত্রিয়েরা চিরকাল রাজসরকারের প্রসাদভোজী, সেই দাসের রক্তই তো তোমার শরীরে।
মা সর্পিণীর মত ফণা তুলিয়া উঠিলেন, বলিলেন, কি বললি? এত বড় কথা তোর? তা, তোর দোষ কি, পরের অন্নে যারা মানুষ হয় তাদের কথাটা চিরকাল বড় বড় হয়, সুর পঞ্চমে উঠেই থাকে।
সোমেশ্বর বলিলেন, তোমার কথার উত্তর তুমি নিজেই দিলে, কাকের বাসায় কোকিল মানুষ হয়, সুর তার পঞ্চমে ওঠে, সেটা তার জাতের গুণ, কাক তাতে চিরকাল ক্রুদ্ধ হয়ে থাকে।
ওদিকে তখন তেজচন্দ্র সদরে সাহেবদের নিকট হরদম লোক পাঠাইতেছেন। সে সংবাদ সোমেশ্বরও শুনিলেন, তাঁহার মাও শুনিলেন। সোমেশ্বর গর্জন করিয়া উঠিলেন, রায়হাট ভূমিসাৎ করে দেব, রায়-বংশ নির্বংশ করে দেব আমি।
সত্য বলিতে গেলে, সে গর্জন তাহার শূন্যগর্ভ কাংস্যপাত্রের নিনাদ নয়, তাঁহার অধীনে তখন হাজারে হাজারে সাঁওতাল উন্মত্ত শক্তি লইয়া ইঙ্গিতের অপেক্ষা করিতেছে। সোমেশ্বরের গৌরবর্ণ রূপ, পিঙ্গল চোখ, পিঙ্গল চুল দেখিয়া তাহারা তাঁহাকে দেবতার মত ভক্তি করিত, বলিত, রাঙা-ঠাকুর। সোমেশ্বরের মা পিতৃবংশের মমতায় বিহ্বল হইয়া পুত্রের পা চাপিয়া ধরিলেন। সোমেশ্বর সর্পদষ্টের মত চমকিত হইয়া সরিয়া আসিয়া নিতান্ত অবসন্নের মত বসিয়া পড়িলেন, বলিলেন, তুমি করলে কি মা, এ তুমি করলে কি? বাপের বংশের মমতায় আমার মাথায় বজ্রাঘাতের ব্যবস্থা করলে?
মা ছেলের মাথায় হাত বুলাইয়া লক্ষ আশীর্বাদ করিলেন, ছেলে তাহাতে বুঝিল না। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সোমেশ্বর বলিলেন, এ পাপের স্থান নেই মা, তবে তুমি নিশ্চিন্ত থাক, রায়-বংশের কেশাগ্র কেউ স্পর্শ করবে না।
সেই রাতেই তিনি নীরবে গোপনে গৃহত্যাগ করিলেন, একবস্ত্রে নিঃসম্বল অবস্থায়, হাতে শুধু এক উলঙ্গ তলোয়ার। ঘর ছাড়িয়া সাঁওতালদের আস্তানা শাল-জঙ্গলের দিকে তিনি অগ্রসর হইতেছিলেন, পিছন হইতে কে বলিল, এত জোরে হাঁটতে যে আমি পারছি না গো? একটু আস্তে চল।
চমকিত হইয়া পিছন ফিরিয়া সোমেশ্বর দেখিলেন, তাহার স্ত্রী শৈবলিনী তাহার পিছন পিছন আসিতেছেন। তিনি স্তম্ভিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন, তুমি কোথায় যাবে?
শৈবলিনী প্রশ্ন করিলেন, আমি কোথায় থাকব?
কেন, ঘরে মায়ের কাছে!
তার পর যখন সাহেবরা আসবে, তোমায় জব্দ করতে আমায় ধরে নিয়ে যাবে?
হুঁ। কথাটা সোমেশ্বরের মনে হয় নাই। সম্মুখেই গ্রামের সিদ্ধপীঠ সর্বরক্ষার আশ্রম। সেই আশ্রমে প্রবেশ করিয়া সোমেশ্বর বলিলেন, দাঁড়াও, ভেবে দেখি। খোকাকে রেখে এলে! যেন সেটাও তাহার মনঃপূত হয় নাই।
শৈবলিনী বলিলেন, সে তো মায়ের কাছে। মাকে তো জাগাতে পারলাম না!
বহুক্ষণ পদচারণা করিয়া সোমেশ্বর বলিলেন, হয়েছে। মায়ের কাছ ছাড়া আর রক্ষা পাবার স্থান নাই। এইখানেই তুমি থাকবে।
বিস্মিত হইয়া শৈবলিনী স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন, এখানে লুকিয়ে থাকবার মত জায়গা আছে নাকি?
আছে। ভক্তিভরে মাকে প্রণাম কর, আশ্রয় ভিক্ষা কর। মাকে অবিশ্বাস করো না।
হিন্দু মেয়ে– প্রায় একশত বৎসরের পূর্বের হিন্দুর মেয়ে এ-কথা মনেপ্রাণেই বিশ্বাস করিত! শৈবলিনী পরম ভক্তিভরে ভূমিলুণ্ঠিত হইয়া প্রণতা হইলেন।
পরমুহূর্তে রক্তাক্ত অসি উদ্যত করিয়া হা-হা করিয়া হাসিয়া অথবা কাঁদিয়া নীরব স্তব্ধ নৈশ আকাশ প্রতিধ্বনিত করিয়া সোমেশ্বর শালজঙ্গলে প্রবেশ করিলেন। শালজঙ্গল তখন মশালের আলোয় অদ্ভুত ভয়াল শ্রী ধারণ করিয়াছে, উপরে নৈশ অন্ধকার, আর অন্ধকারের মত গাঢ় জমাট অখণ্ড নিবিড় বনশ্রী–মধ্যস্থলে আলোকিত শালকাণ্ডের ঘন সন্নিবেশ ও মাটির উপর তাহাদের দীর্ঘ ছায়া, তাহারই মধ্যে প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড জালিয়া সিন্দুরে চিত্রিত মুখ রক্তমুখ দানবের মত হাজার সাঁওতাল। একসঙ্গে প্রায় শতাধিক মাদল বাজিতেছে–ধিতাং ধিতাং ধিতাং ধিতাং। থাকিয়া থাকিয়া হাজার সাঁওতাল একসঙ্গে উল্লাস করিয়া কূক দিয়া উঠিতেছে—উ—র—র! উ—র—র!
সোমেশ্বর হাজার সাঁওতাল লইয়া অগ্রসর হইলেন; একটা থানা লুট করিয়া, গ্রাম পোড়াইয়া, মিশনারিদের একটা আশ্রম ধ্বংস করিয়া, কয়েকজন ইংরেজ নরনারীকে নির্মমভাবে হত্যা করিয়া অগ্রসর হইলেন। পথে ময়ুরাক্ষী নদী। নদীর ওপারে বন্দুকধারী ইংরেজের ফৌজ। সোমেশ্বর আদেশ করিলেন, আর এগোস না যেন, গাছের আড়ালে দাঁড়া।
ও-দিক হইতে ইতিমধ্যে ইংরেজের ফৌজ ভয় দেখাইবার জন্য ফাঁকা আওয়াজ আরম্ভ করিল। সাঁওতালরা সবিস্ময়ে দেখিল, তাহারা অক্ষতই আছে–কাহারও গায়ে একটি আঁচড় পর্যন্ত লাগে নাই। সেই হইল কাল। গুলি আমরা খেয়ে লিলম! বলিয়া উন্মত্ত সাঁওতালদের দল ভরা ময়ুরাক্ষীর বুকে ঝাঁপ দিয়া পড়িল।
মুহূর্তে ও-পারে আবার বন্দুক গর্জন করিয়া উঠিল, এবার ময়ূরাক্ষীর গৈরিক জলস্রোত রাঙা হইয়া গেল–মৃতদেহ ভাসিয়া গেল কুটার মত। সোমেশ্বর চিত্রার্পিতের মতই তটভূমির উপর দাঁড়াইয়া ছিলেন। তিনিও এক সময় তটচ্যুত বৃক্ষের মত ময়ূরাক্ষীর জলে নিপাতিত হইলেন বুকে বিঁধিয়া রাইফেলের গুলি পিঠ ফুড়িয়া বাহির হইয়া গিয়াছিল।
অতঃপর সোমেশ্বরের মা পৌত্র রামেশ্বরকে লইয়া লড়াই করিতে বসিলেন–সরকার বাহাদুরের সঙ্গে। সরকার সোমেশ্বরের অপরাধে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া লইতে চাহিলেন। সোমেশ্বরের মা মকদ্দমা করিলেন–সম্পত্তি তাঁহার, সোমেশ্বরের নয়। আর সরকারবিরোধী সোমেশ্বরকে তিনি ঘরেও রাখেন নাই, সুতরাং সোমেশ্বরের অপরাধে তাঁহার দণ্ড হইতে পারে না।
সরকার হইতে তলব হইল রায়বাবুদের, তাহার মধ্যে তেজচন্দ্র প্রধান। তাঁহাদের কাছে জানিতে চাহিলেন, সোমেশ্বরের মায়ের কথা সত্য কি না। বিদ্রোহী সোমেশ্বরের সহিত সত্যই তিনি কোন সম্বন্ধ রাখেন নাই কি না।
বাড়ি হইতে বাহির হইবার মুখে তেজচন্দ্রের মা বলিলেন, ও বাড়ির ঠাকুরঝি রায়-বংশকে বাঁচাবার জন্য সোমেশ্বরের পায়ে ধরেছিলেন। আমাকেও কি–
তাড়াতাড়ি মায়ের পদধুলি লইয়া তেজচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, তোমার সঙ্গে তো তোমার ঠাকুরঝির পাতানো সম্বন্ধ মা, আমার সঙ্গে যে ওঁর রক্তের সম্বন্ধ।
মা বলিলেন, আশীর্বাদ করি, সেই সুমতিই হোক তোমাদের। কিন্তু কি জান, রায়বাবুদের বোনকে ভালবাসা–কংসের ভালবাসা।
তেজচন্দ্র বলিলেন, চক্রবর্তী জয়দ্রথের গুষ্ঠী মা, শ্যালক-বংশ নাশ করতে ব্যূহমুখে সর্বাগ্রে থাকেন ওঁরা। যাক গে–ফিরে আসি, তার পর বিচার করে যা করতে হয় করো, যা বলতে হয় বলো।
সেখানে রায়-বংশীয়েরা একবাক্যে রায়-বংশের কন্যাকে সমর্থন করিয়া আসিলেন। তেজচন্দ্রের জননীকে কিছু বলিতে বা করিতে হইল স্বয়ং সোমেশ্বরের জননীই পৌত্র রামেশ্বরের হাত ধরিয়া রায়-বাড়ির চণ্ডীমণ্ডপে সন্ধ্যারতির সময় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বলিতে তিনি কিছু পারিলেন না, কিন্তু প্রতিজনের মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিলেন। তেজচন্দ্র রামেশ্বরকে কোলে তুলিয়া লইলেন, তাঁহার মা ননদের হাত ধরিয়া বলিলেন, বাড়িতে পায়ের ধুলো দিতে হবে।
বাড়িতে ঢুকিয়া তেজচন্দ্রের মা বলিলেন, রাধি, আসন নিয়ে আয়।
রাধি-রাধারাণী-তেজচন্দ্রের সাত বৎসরের কন্যা। সে একটা কি করিতেছিল, সে জবাব দিল, আমি কি তোমার ঝি না কি? বল না ঝিকে।
কঠোর-স্বরে ঠাকুমা বলিলেন, উঠে আয় বলছি হারামজাদী।
হাসিয়া সোমেশ্বরের মা বলিলেন, কেন ঘাঁটাচ্ছ ভাই বউ; আমাদের বংশের মেয়ের ধারাই ওই। আমরাও তাই– রায়-বাড়ির মেয়ে চিরকেলে জাহবাজ।
তেজচন্দ্রের মা বলিলেন, শ্বশুরবাড়িতে মেয়ের যে কি হাল হবে, তাই আমি ভেবে মরি। ও মেয়ে স্বামীর নাকে দড়ি দিয়ে ওঠাবে বসাবে, আর নয় তো শ্বশুরবাড়ির অন্ন ওর কপালে নেই।
সোমেশ্বরের মা একবার রাধারাণীকে ডাকিলেন, ও নাতনী, এখানে একবার এস না, একবার তোমায় দেখি, আমিও তোমার ঠাকুমা হই।
সোমেশ্বরের মা রাধারাণীর অপরিচিতা নহেন। কিন্তু এ সংসারে ইষ্টের পরে শত্রুই নাকি মানুষের আরাধ্য বস্তু। সময় সময় ইষ্টকেও ছাপাইয়া শত্ৰু মানুষের মন অধিকার করিয়া থাকে। সেই হেতু সোমেশ্বরের মা, গ্রামের লোক এবং এই বংশের মেয়ে হইয়াও রায়-পরিবারের সকলেরই সম্ভ্রমের পাত্রী। তাঁহাকে দেখিয়া রাধারাণী নিতান্ত ভালমানুষের মত ঝির হাত হইতে আসনখানা টানিয়া লইয়া আগাইয়া আসিল এবং সম্ভ্রমভরেই আসনখানি পাতিয়া দিয়া টিপ করিয়া প্রণাম করিয়া নীরবে যেন আদেশের প্রতীক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।
সোমেশ্বরের মা পরম স্নেহে আদর করিয়া তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া বলিলেন, তোমরা মিথ্যে নিন্দে কর বউ; এমন সুন্দর আর এমন ভাল মেয়ে তো আমি দেখি নি। অ্যাঁ, এ যে বড় ভাল মেয়ে গো।
তেজচন্দ্রের মা সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিলেন, বলিলেন, রাধুকে তা হলে তোমারই পায়ে ঠাঁই দিতে হবে ভাই। আমরা আর কোথায় যাব? রামেশ্বরের সঙ্গে রাধির বিয়ে দেবে, তুমি বল!
সোমেশ্বরের মা এমনটা ঘটিবে প্রত্যাশা করেন নাই, তিনি বিব্রত হইয়া চুপ করিয়া রহিলেন। এই সময়েই রামেশ্বরের হাত ধরিয়া বাড়িতে প্রবেশ করিলেন তেজচন্দ্র। তাঁহার মা বলিলেন, তেজু ধর, পিসীমার পায়ে ধর। ধর বলছি, ধর। খবরদার, ‘হ্যাঁ’ যতক্ষণ না বলবেন, ছাড়বি না। আমি ধরেছি, রামেশ্বরের সঙ্গে রাধুর বিয়ের জন্য।
তেজচন্দ্র পিসীমার পাদস্পর্শ করিয়াই বসিয়া ছিলেন। এ কথাটা শুনিয়া তাঁহারও মন পুলকিত হইয়া উঠিল। রামেশ্বরের সহিত আলাপ করিয়া তাঁহার বড় ভাল লাগিয়াছে। তাহার উপর আজিকার এই প্রণাম আশীর্বাদের বিনিময়ের ফলে মন হইয়াছিল মিলনাকাঙ্খী; কথাটা শুনিবামাত্র তেজচন্দ্র সত্যিই সোমেশ্বরের মায়ের পা জড়াইয়া ধরিলেন।
তেজচন্দ্রের মা বলিলেন, আমি তোমায় মিনতি করছি ঠাকুরঝি,’না’ তুমি বলো না। এ সর্বনেশে ঝগড়ার শেষ হোক, সেতু একটা বাঁধ।
সোমেশ্বরের মায়ের চোখে জল আসিল। তিনি নিজে রায়-বংশের কন্যা, আপনার পিতৃকুলের সহিত এই আক্রোশভরা দ্বন্দ্ব তাঁহারও ভাল লাগে না। চক্রবর্তীদের দ্বন্দ্বে রায়েদের পরাজয় ঘটিলে, অন্তরালে লোকে তাঁহাকে বংশনাশিনী কন্যা বলিয়া অভিহিত করে, সে-সংবাদও তাঁহার অজানা নয়। আর, রামেশ্বর সবেমাত্র দশ বৎসরের বালক, এদিকে তাঁহার জীবন-প্রদীপেও তেল নিঃশেষ হইয়া আসিতেছে; তাঁহার অন্তে রামেশ্বরকে এই রায়-জনাকীর্ণ রায়হাটে দেখিবে কে, এ-ভাবনাও তাঁহার কম নয়। তিনি আর দ্বিধা করিলেন না, সজল চক্ষে বলিলেন, তাই হোক বউ, রামেশ্বরকে তেজচন্দ্রের হাতেই দিলাম।–বলিয়া তিনি রাধারাণীকে কোলে তুলিয়া লইলেন, তাহার কানে কানে বলিলেন, কি ভাই, বর পছন্দ তো?
রাধারাণী রামেশ্বরের দিকে চাহিয়া দেখিয়া আবার সোমেশ্বরের মায়ের কাঁধে মুখ লুকাইয়া বলিল, বাবা, কি কটা চোখ!
সোমেশ্বরের মা হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, রায়-বংশের মেয়ে জব্দ করতে চক্রবর্তী-বংশ সিদ্ধহস্ত। তখন তেজচন্দ্রের বাড়িখানা শঙ্খধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে।
সেতুবন্ধ রচিত হইল।
তেজচন্দ্র যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন সেতুর উপর লোকচলাচলের বিরাম ছিল না। রাধারাণী এ বাড়ি হইতে ও-বাড়ি যাইত আসিত, রামেশ্বর আসিতেন যাইতেন, তেজচন্দ্র স্বয়ং একবেলা রামেশ্বরের কাছারিতে বসিয়া হিসাব-নিকাশ কাগজ-পত্র দেখিতেন, অন্দরে রাধারাণীর মা করিতেন গৃহস্থালির তদারক।
সেকালে উচ্চশিক্ষার সুযোগ তেমন ছিল না, কিন্তু তেজচন্দ্র পুত্রজামাতার শিক্ষার জন্য যথাসাধ্য করিয়াছিলেন। পুঁথি বই সংগ্রহ করিয়া পণ্ডিত মৌলবী দুইজন শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া দিলেন। ইন্দ্রচন্দ্র ফারসীতে পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন, আইনের বইয়ে তিনি ডুবিয়া থাকিতেন। রামেশ্বর পড়িতেন কাব্য।
ইন্দ্রচন্দ্র হাসিয়া বলিতেন, কাব্যে আর প’ড়ো না; জান তো, রসাধিক্য হলে বিকার হয়।
রামেশ্বর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিতেন, আহা বন্ধু, তোমার বাক্য সফল হোক, হোক আমার রসবিকার। রায়-বংশের ‘তন্বীশ্যামা শিখরদর্শনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠি’রা ঘিরে বসুক আমাকে, পদ্মপত্র দিয়ে বীজন করুক, চন্দনরসে অভিষিক্ত করে দিক আমার অঙ্গ–
বাধা দিয়া ইন্দ্রচন্দ্র বলিতেন, থাম, ফক্কড় কোথাকার! রামেশ্বর আপন মনেই আওড়াইতেন, ‘শ্রেণীভারাদলসগমনা স্তোকনম্ৰাস্তনাভ্যাং’। ইহার ফলে সত্যসত্যই রামেশ্বর বয়েসের সঙ্গে সঙ্গে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিলেন। বাড়ির মধ্যে রাধারাণীর, রায়-বাড়ির স্বভাব-মুখরা মেয়ে, কঠোর কলহ-পরায়ণা হইয়া উঠিল। তেজচন্দ্রের পরলোকগমনের পর রায়-বংশের মেয়ে ও চক্রবর্তীবংশের ছেলের কলহ আবার ঘটনাচক্রে উভয় বংশে সংক্রামিত হইয়া পড়িল।
সেদিন রাধারাণী স্বামীর সহিত কলহ করিয়া পিত্রালয়ে চলিয়া আসিয়াছিল। সন্ধ্যায় রামেশ্বর একগাছি বেলফুলের মালা গলায় দিয়া চারিদিকে আতরের সৌরভ ছড়াইতে ছড়াইতে শ্বশুরালয়ে আসিয়া উঠিলেন। ইন্দ্রচন্দ্র তাঁহার সম্ভাষণও করিলেন না, রামেশ্বর নিজেই আসন পরিগ্রহণ করিয়া হাত জোড় করিয়া বলিলেন, নমস্তুভ্যং শ্যালকপ্রবরং কঠোরং কুম্ভবদনং–
বাধা দিয়া ইন্দ্রচন্দ্র বলিলেন, তুমি অতি ইতর!
রামেশ্বর বলিলেন, শ্রেষ্ঠ রস যেহেতু মিষ্ট এবং মিষ্টান্নে যেহেতু ইতরেরই একচেটিয়া অধিকার, সেই হেতু ইতর আখ্যায় ধন্যোহহং। তা হলে মিষ্টান্নের ব্যবস্থা করে ফেল।
আদরের ভগ্নী রাধারাণীর মনোবেদনার হেতু রামেশ্বরকে ইন্দ্র রায় ইহাতেও মার্জনা করিতে পারিলেন, তিনি আর কথা না বাড়াইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। রামেশ্বর আর অপেক্ষা করিলেন না, তিনি উঠিয়া হাসিতে হাসিতে বলেলেন, নাঃ, অরসিকে রস নিবেদনটা নিতান্ত মূর্খতা। চললাম অন্দরে।
বাড়ির ভিতর প্রবেশ করিয়া তিনি ডাকিলেন, কই, সখী মদলেখা কই?
শ্যালক ইন্দ্রচন্দ্রের পত্নী হেমাঙ্গিনীকে তিনি বলিতেন–সখী মদলেখা। তাঁহাদের কথোপকথন হইত মহাকবি বাণভট্টের কাদম্বরীর ভাষায়। স্বয়ং রামেশ্বর তাঁহাদিগকে কাদম্বরী পড়িয়া শুনাইয়াছিলেন।
হেমাঙ্গিনী আদর করিয়া রাধারাণীকে নামকরণ করিয়াছিলেন, কাদম্বরী। রামেশ্বর উত্তর দিয়াছিলেন, তা হ’লে রায়-গিন্নীকে যে নর্মসহচরী ‘মদলেখা’ হতে হয়।
হেমাঙ্গিনী বলিয়াছিলেন, তা হলে আপনি আমাদের ‘চন্দ্রপীড়’ হলেন তো?
কাদম্বরীর সম্বন্ধনির্ণয়-সূত্রানুসারে অবশ্যই হতে হয়; না হয়ে উপায় কি? আর আমার জন্মকুণ্ডলীতেও নাকি লগ্নে আছেন চন্দ্রদেবতা, সুতরাং মিলেও নাকি যাচ্ছে খানিকটা!
খানিকটা বিস্ময় প্রকাশ করিয়া হেমাঙ্গিণী বলিয়াছিলেন, খানিকটা! বিনয় প্রকাশ করছেন যে! রূপে গুণে ষোলআনা মিল যে। রূপের কথা দর্পণেই দেখতে পাবেন। আর গুণেও কম যান না। দিবসে সমস্ত দিনটাই নিদ্রা, উদয় হয় সন্ধ্যার সময়; আর চন্দ্রদেবতার তো সাতাশটি প্রেয়সী, আপনার কথা আপনি জানেন; তবে হার মানবেন না, এটা হলফ করেই বলতে পারি।
সেদিন অর্থাৎ এই নামকরণের দিন, রাধারাণীর অভিমান রামেশ্বর সন্ধ্যাতেই ভাঙাইয়া ছিলেন, কাজেই রাধারাণী এ কথায় উগ্র না হইয়া শ্লেষভরে বলিয়াছিলেন, আমাদের দেশে কুলীনদের ছেলেরা সবাই চন্দ্ৰলগ্নপুরুষ, কারু এক শ বিয়ে, কারু এক শ ষাট। কপালে আগুন কুলীনের!
জোড়হাত করিয়া রামেশ্বর বলিয়াছিলেন, দেবী, সে অপরাধে তো অপরাধী নয় এ দাস। আর আজ থেকে, এই নবচন্দ্ৰাপীড়জন্মে চন্দ্ৰাপীড় দাসখত লিখে দিয়ে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে যে, রাধারাণী-কাদম্বরী ছাড়া সে আর কাউকে জানবে না।
রাধারাণী তর্জনী তুলিয়া শাসন করিয়া বলিয়াছিল, দেখো, মনে থাকবে তো!
আজ রামেশ্বরের আহ্বান শুনিয়া হেমাঙ্গিনী তাঁহাকে সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন, আসুন দেবতা, আসূন।
চাপা-গলায় সশঙ্ক ভঙ্গীতে রামেশ্বর বলিলেন, আপনার দেবী কাদম্বরী কই?
আসন পাতিয়া দিয়া হেমাঙ্গিনী বলিলেন, বসুন। তার পর গভীরভাবে বলিলেন, না চক্রবর্তীমশায়, এবার আপনার নিজেকে শোধরানো উচিত হয়েছে।
একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া রামেশ্বর বলিলেন, চেষ্টা আমি করি রায়গিন্নী, কিন্তু পারি না।
পারি না বললে চলবে কেন? আপনার ব্যবহারে বিতৃষ্ণায় রাধুর চিত্তেই যদি বিকার উপস্থিত হয়, তখন কি করবেন বলুন তো?
রামেশ্বর একদৃষ্টে শ্যালক-পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।
হেমাঙ্গিনী বলিলেন, হুঁ, কেমন মনে হচ্ছে? তার চেয়ে সাবধান হোন এখন থেকে। রাধুর মন আজ যা দেখলাম, তাতে আত্মহত্যা করা কিছুই আশ্চর্য নয়। সময় থাকতে সাবধান হোন।
রামেশ্বর নিজে উচ্ছৃঙ্খলচরিত্র; তিনি হেমাঙ্গিনীর ‘বিকার’ শব্দের নূতন বিশ্লেষণ গ্রহণ করিতে পারিলেন। বিকার শব্দের যে অর্থ তিনি গ্রহণ করিলেন, শাস্ত্র সেই অর্থই অনুমোদন করে, এবং বর্তমান ক্ষেত্রে সেই বিকার হওয়াই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক-শাস্ত্রসসম্মত। কিন্তু তিনি রাগ করিতে পারিলেন না, শাস্ত্রে তিনি সুপণ্ডিত, মনে মনে তিনি অপরাধ স্বীকার করিয়া বলিলেন, রায়-গিন্নী, হয় নিজেকে সংশোধন করব, নয় ব্রাহ্মণের উপবীত পরিত্যাগ করব।
হেমাঙ্গিনী আশ্বস্ত হইয়া এইবার হাসিমুখে বলিলেন, তবে চলুন চন্দ্ৰাপীড়, দেবী কাদম্বরী মান-ও বিরহতাপিতা হয়ে হিমগৃহে অবস্থান করছেন। আসুন, অধীনী মদলেখা এখনই আপনাকে সেখানে নিয়ে যাবে।
দোতালার লম্বা দরদালানে প্রবেশদ্বারের সম্মুখেই মায়ের ঘরে রাধারাণী শুইয়া ছিল। মায়ের মৃত্যুর পর ঘরখানি বন্ধই থাকে, রাধারাণী আসিলে সে-ই ব্যবহার করে। দরদালানে প্রবেশ করিয়াই রামেশ্বর থমকিয়া দাঁড়াইলেন। রাধারাণীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া একটি তরুণকান্তি যুবক কি একখানা বই পড়িয়া রাধারাণীকে শুনাইতেছে।
ওটি কে, রায়-গিন্নী?
রামেশ্বরের সচকিত ভাব দেখিয়া হেমাঙ্গিনী কৌতুকপ্রবণা হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, দেব, উপেক্ষিতা কাদম্বরী দেবীর মনোরঞ্জনের জন্য সম্প্রতি এই তরুণকান্তি কেয়ূরকে আমরা নিযুক্ত করেছি।
ছেলেটি রাধারাণীর পিসতুতো ভাই! পিতৃমাতৃহীন হইয়া সে মামার বাড়িতে আশ্রয় লইতে আসিয়াছে আজই।
ইহার পর সমস্ত ঘটনা রহস্যের আবরণে আবৃত, সেইজন্যই সংক্ষিপ্ত। জানেন একমাত্র রামেশ্বর আর রাধারাণী। তবে ইহার পরদিন হইতে সেতুতে ফাটল ধরিল। রাধারাণীর পিত্রালয়ে আসা বন্ধ হইয়া গেল। রামেশ্বর নিজে হইয়া উঠিলেন কঠোর নিষ্ঠাপরায়ণ ব্রাহ্মণ, অন্য দিক দিয়া একাগ্রচিত্তে বিষয় অনুরাগী। বাল্যকালে রামেশ্বরের যে পিঙ্গল চোখ দেখিয়া রাধারাণী ভয় পাইয়াছিল, সে চোখ কৌতুক-সরসতা হারাইয়া এমন তীব্র হইয়া উঠিল যে রাধারাণী ভয় না করিয়া পারিল না। ওদিকে রায়-বংশের সহিত আবার খুঁটিনাটি আরম্ভ হইয়া গেল। পরস্পরের যাওয়া-আসা সংক্ষিপ্ত হইয়া অবশিষ্ট রহিল কেবল লৌকিকতাটুকু। ইহার বৎসরখানেক পরে রাধারাণী একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিল। কিন্তু মাসখানেক পর অকস্মাৎ সন্তানটি মারা গেল; কয়েকদিন পরই একদিন রাত্রে রাধারাণীও হইল নিরুদ্দিষ্ট! প্রথমে সকলে ভাবিয়াছিল রাধারাণী বোধ হয় আত্মহত্যা করিয়াছে। ইন্দ্র রায় সন্দেহ করিয়াছিলেন, রাধুকে হত্যা করিয়াছে রামেশ্বর। কিন্তু রাধারাণীর সন্ধান পাওয়া গেল দশ মাইল দূরবর্তী রেলস্টেশনের পথে। একজন চাষী বলিল, রায়বাড়ির মেয়ে রাধু দিদিঠাকরুণকে রেলস্টেশনের পথে দেখিয়াছে। তিনি তাহাকে স্টেশন কতদূর জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। সে কথাটা কাহাকেও সাহস করিয়া বলে নাই। ইহার পর রাধারাণীর গৃহত্যাগে আর কাহারও সন্দেহ রহিল না।
লজ্জায় রায়-বংশের মাথা কাটা গেল। রামেশ্বর আবার বিবাহ করিলেন পশ্চিম-প্রবাসী এক শিক্ষক কন্যা সুনীতিকে। মহীন্দ্র এবং অহীন্দ্র দুইটি সন্তান সুনীতির। তারপর রামেশ্বর এই কয়েক বৎসর পূর্বে অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। আজ দুই বৎসর একরূপ শয্যাশায়ী হইয়া একেবারে ঘরে ঢুকিয়া বসিয়াছেন। আপনার মনে মৃদুস্বরে কথা বলেন আর চুপ করিয়া বিছানায় বসিয়া থাকেন।
এই হল রায়-বংশ এবং চক্রবর্তী-বংশের ইতিহাস। এই সম্বন্ধেই সুনীতি ইন্দ্র রায়কে বলেন, ও-বাড়ির দাদা।
সুনীতি সেদিন অপরাহ্নে অহীন্দ্রকে বলিলেন, তুই যাবি একবার ও-বাড়ির দাদার কাছে? অহি বলিল, কি বলব?
বলবি, সুনীতি খানিকটা চিন্তা করিয়া লইলেন। তারপর বলিলেন, নাঃ, থাক অহি, মজুমদার ঠাকুরপো আর মহী ফিরেই আসুক। আবার কি বলবেন রায়-বাবুরা, তার চেয়ে থাক।
অহি বলিল, ঐ তোমাদের এক ভয়। মানুষকে বিনা কারণে অপমান করা কি এতই সোজা মা? মহাত্মা গান্ধী সাউথ আফ্রিকায় কি করেছিলেন জান? সেখানে ইংরেজরা রাস্তার যে-ধারে যেত, রাস্তার সে ধারে কালা আদমীকে যেতে দিত না। গেলে অপমান করত, জেল পর্যন্ত হত। মহাত্মাজী সমস্ত অপমান নির্যাতন সহ্য করে সেই রাস্তাতেই যেতে আরম্ভ করলেন। অপমানের ভয়ে বসে থাকলে কি কখনও সেই অধিকার পেত কালা আদমী? বল, কি বলতে হবে?
সুনিতী দেবী শিক্ষকের কন্যা, তাঁহার বড় ভাল লাগে এই ধারার আদর্শনিষ্ঠার কথা। তিনি ছেলের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, বেশ, তবে যা, গিয়ে বলবি, এই যে এত বড় গ্রাম জুড়ে বিবাদ–এটা কি ভাল? আপনি এখন গ্রামের প্রধান ব্যক্তি, আপনিই এটা মিটিয়ে দেন। তবে গরীব প্রজা যেন কোনমতেই মারা না পড়ে, সেইটে দেখবেন, এই কথাটা মা বিশেষ করে বলে দিয়েছেন।
ইন্দ্র রায় কাছারী-ঘরে বসিয়া কথা বলিতেছিলেন একজন মহাজনের সঙ্গে। ঐ চর লইয়াই কথা। মহাজনের বক্তব্য, পাঁচশত টাকা নজরস্বরূপ গ্রহণ করিয়া রায় মহাশয় তাহার দাবি স্বীকার করুন।
ইন্দ্র রায় হাসিয়া বলিলেন, চরটা অন্ততঃ পাঁচ শ বিঘে, দশ টাকা বিঘে সেলামী নিয়ে বন্দোবস্ত করলেও যে পাঁচ হাজার টাকা হবে দত্ত, আর এক টাকা বিঘে খাজনা হলেও বছরে পাঁচ শ টাকা খাজনা।
কিন্তু সে তো মামলা-মকদ্দমার কথা হুজুর।
ডিক্রি তো আমি পাবই, আর ডিক্রি হলে খরচাও পাব। সুতরাং লোকসান করতে যাবার কোন কারণ নেই আমার।
মহাজন চিন্তা করিয়া বলিল, আমি আপনাকে হাজার টাকা দেব, আর খাজনা ওই পাঁচ শ টাকা। অগ্রিম বরং আমি পাঁচশ টাকা দিচ্ছি। চারদিন পর আসব আমি।
নিস্পৃহতার সহিত রায় বাঁ হাতে গোঁফে তা দিতে দিতে বলিলেন, ভাল, এস।
লোকটি চলিয়া যাইতেই রায় বাহিরে আসিলেন। অহীন্দ্র তাঁহার অপেক্ষাতেই বাহিরেই বসিয়া ছিল। অহীন্দ্রকে দেখিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। অহি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিল, আমার মা আপনার কাছে পাঠালেন।
তুমি রামেশ্বর চক্রবর্তীর ছেলে না? রায়েরা চক্রবর্তীদের কখনও বাবু বলে না।
হ্যাঁ।
হুঁ, চোখ আর চুল দেখেই চেনা যায়। রামেশ্বরের কোন ছেলে তুমি? রায়ের সকল কথার মধ্যে তাচ্ছিল্যের একটা সুর তীক্ষ্ণ সূচিকার মত মানুষকে যেন বিদ্ধ করে। কিন্তু সমস্ত উপেক্ষা করিয়া হাসিয়া স্বচ্ছন্দে সরল ভঙ্গীতে অহি উত্তর দিল, আমি তাঁর ছোট ছেলে
কি কর তুমি? পড়, না পড়া ছেড়ে দিয়েছ?
না, আমি ফার্স্ট ক্লাসে পড়ি-শহরের স্কুলে।
রায় বিস্মিত হইয়া বলিলেন, ফার্স্ট ক্লাসে পড় তুমি? কিন্তু বয়স যে তোমার অত্যন্ত কম! বাঃ, বড় ভাল ছেলে তুমি! তা তোমার বাপও যে খুব বুদ্ধিমান লোক ছিল। কিন্তু তোমার বড় ভাই, কি নাম তার? সে তো শুনেছি পড়াশুনা কিছু করে নি। স্কুলে তো তার খারাপ ছেলে বলে অখ্যাতিই ছিল, মাস্টার বলেছিলেন আমাকে।
অহি স্থিরদৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, আমার কথাগুলি একবার শুনে নিন।
হাসিয়া রায় বলিলেন, তুমি তো বলবে ঐ চরটার কথা?
হ্যাঁ।
দেখ, ও-চরটা আমার। অবশ্য আমার জ্ঞানবুদ্ধিমত। এই কথাই বলবে তোমার মাকে।
বেশ, তাই বলব। তবে মায়ের অনুরোধ ছিল, যেন প্রজাদের ওপর কোন অবিচার না হয়, সেইটে আপনি দেখবেন।
রায় এ কথার কোন জবাব দিলেন না। অহীন্দ্র আর অপেক্ষা না করিয়া গমনোদ্যত হইয়া বলিল, তা হলে আমি আসি।
সে কি? একটু জল খেয়ে যাও।
না, জল খেয়েই বেরিয়েছি, চরের দিকটায় একটু বেড়াতে যাব।
রায় বলিলেন, শোন। তখন অহীন্দ্র কতকটা অগ্রসর হইয়াছে। অহীন্দ্র দাঁড়াইল, রায় বলিলেন, চরের ওপারটায় শুনেছি বড় সাপের উপদ্রব। তোমার না যাওয়াই ভাল।
অহীন্দ্র সবিনয়ে বলিল, আচ্ছা, আমি ভেতরে যাব না।
.
০৩.
ইন্দ্র রায় সত্যই বলেছিলেন, চরটা কীট-পতঙ্গ-সরীসৃপে পরিপূর্ণ।
গ্রামের কোলেই কালিন্দী নদীর অগভীর জলস্রোত পার হইয়া খানিকটা বালি ও পলিমাটিতে মিশানো তৃণহীন স্থান, তার পরেই আরম্ভ হইয়াছে চর। সমগ্র চরটা বেনাঘাস আর কাশের ঘন জঙ্গলে একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া আছে। তাহারই মধ্যে বাসা বাঁধিয়া আছে-অসংখ্য প্রকারের কীট-পতঙ্গ আর সাক্ষাৎ মৃত্যুদূতের মত ভয়ঙ্কর নানা ধরনের বিষধর সাপ।
প্রৌঢ় রংলাল মণ্ডল বলিল, এই তো ক বছর হল গো বাবু মশায়, একটা বাছুর কি রকম ছটকিয়ে গিয়ে পড়েছিল চরের উপর। বাস্, আর যায় কোথা, ইয়া এক পাহাড়ে চিতি-ধরলে পিছনের ঠ্যাঙে। আঃ, সে কি বাছুরটার চেঁচানি! বাস্, বার কতক চেঁচানির পরই ধরলে পাক দিয়ে জড়িয়ে। দেখতে দেখতে বাছুরটা হয়ে গেল ময়দার নেচির মত লম্বা। কিন্তু কারু সাহস হল না যে এগিয়ে যাই।
অহীন্দ্র প্রশ্ন করিল, আচ্ছা, আগে নাকি ওই চরের ওপরেই ছিল কালী নদী?
হ্যাঁ গো। ঠিক ওই চরের মাঝখানে। লদীর ঘাট থেকে গেরাম ছিল একপো রাস্তার ওপর। বোশেখ মাসে দুপুরবেলায় লদীর ঘাটে আসতে পায়ে ফোস্কা পড়ে যেত।
তুমি দেখেছ?
অহীন্দ্রের ছেলেমানুষিতে কৌতুক অনুভব করিয়াই যেন রংলাল বলিল, আই দেখেন, দাদাবাবু আবার বলেন কি দেখ। কালী নদীর ধারেই-ওই দেখেন, চরের পরই যেখানে চোরাবালি-ওইখানে আমাদের পঁচিশ কাঠা আওয়াল জমি ছিল, তারপর ওই চর যেখানে আরম্ভ হয়েছে-ওইখানে ছিল গো-চর নদীর ওলা। ছেলেবেলায় আমি ওইখানেই গরু চরিয়েছি! ওই জমিতে আমি নিজে লাঙল চষেছি। তখন আমাদের গরু ছিল কি মশায়-এই হাতির মত বলদ। আর রতন কামারের গড়া ফাল-একহাত মাটি একেবারে দু ফাঁক হয়ে যেত। আঃ! মাটিরই বা কি রঙ-একেবারে লাল-সেরাক!
বৃদ্ধ চাষী মনের আবেগে পুরাতন স্মৃতিকথা বলিয়া যায়, অহীন্দ্র কালী নদীর তটভূমিতে চরের প্রান্তভাগে বসিয়া চরের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া শুনিয়া যায়। বৃদ্ধ বলে, কালী নদীর একেবারে তটভূমিতে সে কি নধর কচি ঘাস গালিচার মত পুরু হইয়া থাকিত, সারা গ্রামের গরু খাইয়া শেষ করিতে পারিত না। তাহার পর ছিল তরির জমি। সে আমলে তুতপাতার চাষ ছিল একটা প্রধান চাষ। জবগাছের পাতার মত তুঁতের পাতা। চাষীরা বাড়িতে গুটিপোকা পালন করিত,– গুটিপোকার খাদ্য এই তুঁতপাতা। যে চাষী গুটিপোকা পালন করিত না, তুঁতগাছের চাষ করিত, তুঁতপাতা বিক্রয় করিয়াও সেও দশ টাকা রোজগার করিত। তখন গ্রামেরই বা শোভা কি! বাবুরাই বা কি সব, এক-একজন দিকপাল যেন। ছাতি কি বুকের! রংলাল বলিল, আপনকার কত্তাবাবা, বাপ রে, বাপ রে, ‘রংলাল’ বলে হেঁকেছেন তো জান একেবারে খাঁচাছাড়া হয়ে যেত।
অহীন্দ্র চরের উপর দৃষ্টি রাখিয়াই প্রশ্ন করিল, আচ্ছা, কোন্ বছর কালী প্রথম এ-কূল ভাঙল, তোমার মনে আছে!
পিতামহ-প্রপিতামহের ইতিহাস সে বহুবার শুনিয়াছে, আর ওই চরটাই তাহার মন অধিকার করিয়া আছে। নদীর বুকে নাকি ব- দ্বীপগুলি এবং নদী-সাগর-সঙ্গমের মুখে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপগুলি হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া পলি জমিয়া জমিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে, উঠিতেছে এবং উঠিবে। বাংলার নিম্নাংশটা গোটাই নাকি এমনই করিয়া জলতল হইতে উঠিয়াছে। কত প্রবালকীট, কত শুক্তি-শামুকের দেহ পলির স্তরে স্তরে চাপা পড়িয়া আছে! ভূগোলের মাস্টার কৃষ্ণবাবু কি চমৎকারই না কথাগুলি বলেন!
রংলাল বলিল, কালী তো আমাদের সামান্য নদী লয় দাদাবাবু, উনি হলেন সাক্ষাৎ যমের ভগ্নী। কবে থেকে যে উনি রায়হাটের কূল তলে তলে খেতে আরম্ভ করেছেন, তা কে বলবে বলেন! তবে উনি যে কালে হাত বাড়িয়েছেন, তখন আপনার রায়হাট উনি আর রাখবেন না। বললাম যে, যমের ভগ্নী উনি। বুঝলেন কালী যাকে নিলে, কার সাধ্যি তাকে বাঁচায়! কত গেরাম যে উনি খেয়েছেন, তার আর ঠিক-ঠিকেনা নাই। ফি বছর দেখবে, কত চাল, কত কাঠ, কত গরু, কত মানুষ কালীর বানে ভেসে চলেছে যমের বাড়ি। একবার সাক্ষাৎ পেত্যক্ষ করেছি আমি। তখন আমার জোয়ান বয়েস; দেখলাম, একখানা ঘরের চালের ওপর বসে ভেসে যাচ্ছে একটি মেয়ে, কোলে তার কচি ছেলে। উঃ, কি তার কান্না, সে কান্নায় গাছপাথর কাঁদে দাদাবাবু! আমি মশাই ঝাঁপিয়ে পড়লাম আমাদের সরু লৌকো নিয়ে, সঙ্গে নিলাম কাছি। একে স্রোতের মুখে, তার ওপর কষে ঠেল মারলাম দাঁড়ের। সোঁ সোঁ করে গিয়ে পড়লাম চালের কাছে। আঃ, তখন মেয়েটির কি মুখের হাসি! সে বুঝল আমি বাঁচলাম। মশায়, বলব কি, ঠিক সেই সময়েই উঠল একটা ঘুরনচাকি, আর বাস্, বোঁ ক’রে ঘুরপাক মেরে নিলে একেবারে চালসুদ্ধ পেটের ভেতর ভরে। কলকল করে জল যেন ডেকে উঠল, বলব কি দাদাবাবু, ঠিক যেন খলখল করে হেসে উঠলে কালী। সে হাতজোড় করিয়া কপালে ঠেকাইয়া উদ্দেশে কালীকে প্রণাম করিল। সে বলিল, অ্যাই, সেই বছরেই দেখলাম, কালী-মা এই কূল দিয়ে চলেছেন।
সেই বৎসরেই শীতকালে দেখা গেল, কালীর অগভীর জলস্রোত ওপারের দিকে বালি ঠেলিয়া দিয়া রায়হাটের কোল ঘেঁষিয়া আসিয়া প্রবাহিত হইতেছে। তার পর বৎসরের পর বৎসর ও-পাশে জমিতে আরম্ভ করিল বালি পড়িতে আর এদিক হইল গভীর। বর্ষার যখন কালী হইত দুকূলপ্লাবী, তখন কিন্তু এপার হইতে ওপার পর্যন্ত জল ছাড়া কিছুই দেখা যাইত না। তখন ওপারটা ছিল ছয় মাস জল আর ছয় মাস বালির স্তূপ। তার পর প্রথমেই গ্রাস করিল এপারের গো-চারণের জন্য নির্দিষ্ট তৃণশ্যামল তটভূমিটুকু। ওপারে তখন হইতে বর্ষার শেষে বালির উপর পাতলা পলির স্তর জমিতে আরম্ভ করিল।
রংলাল বলিল, বুঝলেন দাদ্যবাবু, শুধু কি পলি; রাজ্যের জিনিস-এই আপনার খড়কুটো ঘাসপাতা যা খেতেন কালী, এসে উগড়ে দিতেন এই চরের ওপর। আর তার ওপর দিতেন মাটি আর বালি চাপা।
বলিতে বলিতে বৃদ্ধ চাষীর মনে যেন দার্শনিকতার উচ্ছ্বাস জাগিয়া উঠিল, সে বলিল, এই আমাদের মেয়েগুলো খেলে দেখেন না, ভিজে বালির ভেতর পা পুরে তার ওপর বালি চাপিয়ে চাপড়িয়ে চাপড়িয়ে পা-টি বের করে নেয়, কেমন ঘর হয়! আবার মনে হয় লাথি মেরে– ভাঙে আর বলে, হাতের সুখে গড়লাম, আর পায়ের সুখে ভাঙলাম। কালীও আমাদের তাই– ভাঙতে যেমন, আর গড়তেও তেমন। উঃ, কত কী যে এসে জমা হত দাদাবাবু, শামুক-গুগলি-ঝিনুক সে সব কত রকমের, বাহার কি সব! খরার সময় সব সেঁতানি শুকিয়ে কাঠ হয়ে যেত, তখন ছেলেমেয়েরা চরের ধারে ধারে সে-সব ঝিনুক কুড়োতে যেত। ছোট ছোট ঝিনুকে ঘামাচি মারত সব পুটপাট করে। কেউ কেউ লক্ষীবেদীতে বসিয়ে বসিয়ে আলপনার মত লতাপাতা তৈরি করত। তখন আপনার জলথল পড়লে খুদি খুদি ঘাস হত এই আপনার গরুর রোঁয়ার মত।
কালী ঠিক যেন বালিকার মত খেলাঘর পাতিয়াছিল ওইখানে। বালিকার মত যেখানে যাহা পাইত, আনিয়া ওইখানে জড় করিয়া রাখিত। আর তার উপর চাপা দিত বালি আর পলি।
অহীন্দ্র আবার প্রশ্ন করিল, আচ্ছা, তোমরা সব তখন এই চর কার তা মীমাংসা করে নাও নি কেন?
রংলাল অহীন্দ্রের নির্বুদ্ধিতায় হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল, অ্যাই দেখেন, দাদাবাবু কি বলেন দেখেন। তখন উ চর নিয়ে লোকে করবে কি? এই এখানে খানিক খাল, চোরাবালি, ওখানে বালির টিপি; আর যে পোকার ধুম। ছোটলোকের মেয়েরা পর্যন্ত কাঠকুটো কুড়োতে চরের ভেতর যেত না। বুঝলেন, খুদি খুদি পোকায় একেবারে অষ্টাঙ্গ ছেঁকে ধরত। তার আবার জ্বালা কি, ফুলে উঠত শরীর।
চৈত্র মাসের অপরাহ্ন; সূর্য পশ্চিমাকাশে রক্তাভ হইয়া অস্তাচলের সমীপবর্তী হইতে চলিয়াছে। কালীর ওপারে রায়হাটে তটভূমিতে বড় বড় গাছ। শিমূলগাছই বেশী, শিমূলের নিঃশেষে পত্রহীন শাখা-প্রশাখার সর্বাঙ্গ ভরিয়া রক্ত-রাঙা ফুলের সমারোহ। পালদে গাছগুলিও তাই, পত্ররিক্ত এবং শিমূলের চেয়েও গাঢ় রক্তবর্ণের পুষ্পসম্ভারে সমৃদ্ধ। বসন্তের বাতাসে কোথা হইতে একটি অতি মধুর গন্ধ আসিয়া শ্বাসযন্ত্র ভরিয়া দিল।
অহীন্দ্র বার বার গন্ধটি গ্রহণ করিয়া বলিল, কি ফুলের গন্ধ বল তো?
নিতান্ত তাচ্ছিল্যের সহিত রংলাল বলিল, উ ওই চরের মধ্যে কোন ফুল-টুল ফুটে থাকবে ওর কি কেউ নাম জানে। কোথা থেকে কি এনে কালী যে লাগান ওখানে, ও এক ওই কালীই জানেন। বুঝলেন, এই প্রথম বার যে বার-ঘাস বেশ ভাল রকমের হল, আমরা গরু চরাব বলে দেখতে এসেছিলেম।
বলিতে বলিতে রংলালের মুখে সেই দিনের সেই বিস্ময় ফুটিয়া উঠে, সে বলিয়া যায়, কত রকমের নাম-না-জানা চোখে-না-দেখা ছোট ছোট লতা-গাছ-ঘাস ওই চরের উপর তখন যে জন্মিয়াছিল, তাহার আর ইয়াত্তা নাই। আর ঘাসে পা দিলেই লাফাইয়া উঠিত ফড়িং-জাতীয় শত শত কীট, উপড়ে উড়িয়া বেড়াইত হাজারো রকমের প্রজাপতি ফড়িং। তার পর জন্মিয়াছে ওই বেনাঘাস আর কাশগুল্ম। কিন্তু উহার ভিতরে ভিতরে কত যে গাছ, কত যে লতা আত্মগোপন করিয়া আছে, তাহার সংখ্যা কি কেহ জানে? আর ওই সব মধুগন্ধী গাছের গোড়ায় বাসা বাঁধিয়াছে কত বিষধর–! বলিতে বলিতে রংলাল শিহরিয়া উঠিল, বলিল, খবরদার দাদাবাবু, কখনও যেন গন্ধের লোভে ভিতরে ঢুকবেন না। বরং ও সাঁওতাল বেটাদের বলবেন, ওরা ঠিক জানে সব, কোথা কি আছে। ফুলের ওপর ওদের খুব ঝোঁক তো!
অকস্মাৎ বৃদ্ধ রংলাল মহা উৎসাহিত হইয়া উঠিল, বলিল, যাবেন দাদাবাবু সাঁওতালপাড়ায়? আ-হা হা, কি ফসলই সব লাগিয়েছে, অঃ, আলু হয়েছে কি, ইয়া মোটা মোটা! বরবটি শুঁটি আপনার আধা হাত করে লম্বা! সাধে কি আর গাঁসুদ্ধ নোক হঠাৎ ক্ষেপে উঠল দাদাবাবু!
অহি আশ্চর্য হইয়া বলিল, সাঁওতাল কোথায়? ওরা তো থাকে অনেক দূরে পাহাড়ের ওপর।
ঘাড় নাড়িয়া রংলাল বলিল, অ্যাই দেখেন, আপনি কিছুই জানেন না। চরে যে সাঁওতাল বসেছে গো? উই দেখেন, ধোঁয়া উঠছে না! বেটারা সব রান্না চড়িয়েছে। ওরাই তো চোখ ফুটিয়ে দিলে গো। আমাদের বাঙালী জাতের সাধ্যি কি, এই বন কেটে আর ওই সব জন্তুজানোয়ার মেরে এখানে চাষ করে! ওরা কিন্তু ঠিক বেছে বেছে আসল জায়গাটি এসে ধরেছে। কোথা থেকে এল আর কবে এল-কেউ জানে না, ওরা আপনিই এসেছে, আপন মগজেই খানিকটা জায়গা-জমি সাফ করে বসেছে, চাষ করছে, এইবার সব ঘর তুলেছে। গাঁয়ের লোক তো জানলে, ওখানে মাঝি বসেছে, চাষ হচ্ছে। সেই দেখেই তো চোখ ফুটলো সব। বাস, আর যায় কোথা, লেগে গেল ফাটাফাটি! জমিদার বলছে চর আমাদের; আমরা চাষীরা বলছি, ইপারে আমাদের জমি গিয়ে ওপারে চর উঠেছে, চর আমাদের। আসল ব্যাপারটা হল– ওই সাঁওতালরা ওখানে সোনা ফলাচ্ছে, বুঝলেন?
অহীন্দ্র অগ্রসর হইয়া বলিল, চল, যাব। কোন্ দিকে?
ওই দেখেন, বেনার ঝোপ থেকে মাঝিনদের দল বেরিয়েছে লদীতে জল আনতে।
অহীন্দ্র দেখিল, গাঢ় সবুজ বেনাবনের মধ্য হইতে বাহির হইতেছে আট-দশটি কালো মেয়ের সারি, মাথায় কলসী লইয়া একটানা সুরে গান গাহিতে গাহিতে তাহারা নদীর দিকে চলিয়াছে।
দুই পাশে এক বুক কাশ ও বেনাঘাসের জঙ্গল। তাহারই মধ্য দিয়া স্বল্পপরিসর পরিচ্ছন্ন একটি পথ সর্পিল ভঙ্গিতে চরের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে। ঘাসের বনের মধ্যে নানা ধরনের অসংখ্য লতা ও গাছ জন্মিয়াছে; গুচ্ছ গুচ্ছ বেনাঘাস অবলম্বন করিয়া লতাগুলি লতাইয়া লইয়া ঘাসের মাথায় যেন আচ্ছাদনী প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে! সাপের ফণার মত উদ্যত বঙ্কিম ডগাগুলি স্থানে স্থানে একেবারে পথের উপরে আসিয়া পড়িয়াছে, মানুষের গায়ে ঠেকিয়া সেগুলি দোল খায়। মাঝে মাঝে চৈত্রের উতলা বাতাস আসিয়া ঘাসের জঙ্গলের এক প্রান্ত পর্যন্ত অবনত করিয়া দিয়া যেন ঢেউয়ের পর ঢেউ তুলিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে বিচিত্র সরসর সনসন শব্দ।
রংলাল একটা লতার ভাঁটা টানিয়া ছিঁড়িয়া লইয়া বলিল, অঃ, অনন্তমূল হয়েছে দেখ দেখি! কত যে লতা আছে!
অহীন্দ্র এই পথটির পরিচ্ছনতা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া সাঁওতালদের কথা ভাবিতেছিল–এমন কালো জাতি, অথচ কি মসৃণ পরিচ্ছনতা ইহাদের জীবনে! কোথায় যেন বনান্তরালে কোলাহল শুনা যাইতেছে। চারিদিকে চাহিয়া অহীন্দ্র দেখিল, একেবারে ডানদিকে কতকগুলি কুঁড়েঘরের মাথা জাগিয়া আছে। পথে একটা বাঁক পার হইয়াই সহসা যেন তাঁহারা পল্লীর মধ্যে আসিয়া পড়িল।
ঘাসের জঙ্গল অতি নিপুণভাবে পরিষ্কার করিয়া ফেলিয়া তাহারই মধ্যে দশ-বারো ঘর আদিম অর্ধ উলঙ্গ কৃষ্ণবর্ণ মানুষ বসতি বাঁধিয়াছে। ঘর এখনও গড়িয়া উঠে নাই, সাময়িকভাবে চালা বাঁধিয়া, চারিদিকে বেড়া দিয়া তাহার উপর মাটির প্রলেপ লাগাইয়া তাহারই মধ্যে এখন তাহারা বাস করিতেছে। আশপাশের মাটির দেওয়াল দিয়া স্থায়ী ঘরের পত্তনও শুরু হইয়াছে। প্রত্যেক ঘরের সম্মুখে গোবর ও মাটি দিয়া নিকানো পরিচ্ছন্ন উঠান। উঠানের পাশে পৃথক পৃথক্ আঁটিতে বাঁধা নানা প্রকার শস্যের বোঝা। বরবটির লতা, আলুগুলি ছাড়াইয়া লইয়া সেই গাছগুলি, মুসুরির ঝাড়, ছোলার ঝাড় সবই পৃথক্ পৃথক্ ভাবে রক্ষিত; দেখিয়া অহীন্দ্র মুগ্ধ হইয়া গেল।
রংলাল ডাকিয়া বলিল, কই, মোড়ল মাঝি কই রে? কে এসেছে দেখ!
কে বেটে?–তু কে বেটিস?–বলিতে বলিতে বাহির হইয়া আসিল এক কৃষ্ণকায় সচল প্রস্থরখণ্ড। আকৃতির চেয়ে আকারটাই তাহার বড় এবং সেইটাই চোখে পড়িয়া মানুষকে বিস্মিত করিয়া দেয়। পেশীর পুষ্টিতে এবং দৃঢ়তা ও বিপুলতায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি যেন খর্ব হইয়া গিয়াছে; লোকটি সবিস্ময়ে উগ্র-গৌরবর্ণের কৃশকায় দীর্ঘতনু বালকটিকে দেখিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।
রংলাল বলিল, তোর তো অনেক বয়স হল, তোদের রাঙাঠাকুরের নাম জানিস? তোদের সাঁওতালী হাঙ্গামার সময়–
রংলালকে আর বলিতে হইল না, বিশাল বিন্ধ্যপর্বত যেন অগস্ত্যের চরণে সাষ্টাঙ্গে ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িল।
রংলাল বলিল, ইনি তাঁর লাতি- ছেলের ছেলে, বেটার বেটা।
মাঝি আপন ভাষায় ব্যস্তভাবে আদেশ করিল, চৌপায়া নিয়ে আয়, শিগগির!
ছোট্ট টুলের আকারে দড়ি দিয়া বোনা বসিবার আসনে অহীন্দ্রকে বসাইয়া মাঝি তাহার সম্মুখে মাটির উপর উবু হইয়া হাত দুইটি জোড় করিয়া বসিয়া অহীন্দ্রকে দেখিতে দেখিতে বলিল, হুঁ ঠিক সেই পারা, তেমুনি মুখ, তেমুনি আগুনের পারা রঙ, তেমুনি চোখ! হুঁ, ঠিক বেটে, ঠিক বলেছিস তু মোড়ল।
রংলাল হাসিয়া বলিল, তুই তাকে দেখেছিস মাঝি?
হুঁ, দেখলাম বৈকি গো। শাল-জঙ্গলে মাদল বাজছিলো, হাঁড়িয়া খাইছিলো সব বড় বড় মাঝিরা, আমরা তখন সব ছোট বেটে; দেখলাম সি, সেই আগুনের আলোতে রাঙাঠাকুর এল।
অহীন্দ্র আশ্চর্য হইয়া প্রশ্ন করিল, তোমার কত বয়স হবে মাঝি?
অনেক চিন্তা করিয়া মাঝি বলিল, সি অনেক হল বৈকি গো, তা তুর দুকুড়ি হবে।
রংলাল হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল, ওদের হিসেব অমনই বটে। তা ওর বয়েস পঁচাত্তর-আশি হবে দাদাবাবু।
পঁচাত্তর-আশি! অহীন্দ্র আশ্চর্য হইয়া গেল, এখনও এই বজ্রের মত শক্তিশালী দেহ! ইতিমধ্যে পাড়ার যত সাঁওতাল এবং ছেলেমেয়েরা অহীন্দ্রের চারিপাশে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া বিস্ময়বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে তাহাকে দেখিতেছিলে। পাড়াময় রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছে, রাঙাঠাকুরের বেটার বেটা আসিয়াছে, আর তিনি নাকি ঠিক রাঙাঠাকুরের মত দেখিতে– আগুনের মত গায়ের রঙ! ভিড়ের সম্মুখেই ছিল মেয়েদের দল। কষ্টিপাথরে খোদাই-করা মূর্তির মত দেহ, তেমনই নিটোল এবং দৃঢ় তৈলমসৃণ কষ্টির মত উজ্জ্বল কালো। পরনে মোটা খাটো কাপড়, মাথার চুলে তেল দিয়া পরিপাটি করিয়া আঁচড়াইয়া এলোখোঁপা বাঁধিয়াছে, সিঁথি উহারা কাটে না, কানে খোঁপায় নানা ধরনের পাতা-সমেত সদ্যফোঁটা বনফুলের স্তবক। অহীন্দ্র অনুভব করিল, সেই গন্ধ এখানে যেন বেশ নিবিড় হইয়া উঠিতেছে।
সে প্রশ্ন করিল, এ কোন ফুলের গন্ধ মাঝি?
মাঝি মেয়েদের মুখের দিকে চাহিল। চার-পাঁচজনে কলরব করিয়া কি বলিয়া উঠিয়া আপন আপন খোঁপা হইতে ফুলের স্তবক খুলিয়া ফেলিল। অহীন্দ্র দেখিল, লবঙ্গের মত ক্ষুদ্র আকারের ফুল, একটি স্তবকে কদম্বকেশরের মত গোল হইয়া অসংখ্য ফুটিয়া আছে। কিন্তু মোড়ল মাঝি গম্ভীর ভাবে কি বলিল। মেয়েগুলি ফুলের স্তবক আবার খোঁপায় গুঁজিয়া সারি বাঁধিয়া ওই দমকা বাতাসের মত ওই বেনাবন ঠেলিয়া কোথায় চলিয়া গেল।
রংলাল বলিল, কি হ’ল? কোথায় গেল সব?
ফুল আনতে, রাঙাবাবুর লেগে।
কেনে, ওই ফুল দিলেই তো হ’ত।
ধ্যুৎ, রাঙাঠাকুরের লাতিকে ওই ফুল দিতে আছে? তুরা দিস?
অহীন্দ্র বলিল, না গেলেই হ’ত মাঝি, কত সাপ আছে চরে? নাই?
তাচ্ছিল্যের সহিত মাঝি বলিল, উ সব সরে যাবে, কুন্ দিকে পালাবে তার ঠিক নাই।
অহীন্দ্র বলিল, এখানে নাকি খুব বড় বড় সাপ আছে?
অহীন্দ্রের কথাকে ঢাকিয়া দিয়া মেয়ের ও ছেলের দল কলরব করিয়া উঠিল। মাঝি হাসিয়া বলিল, আজই একটা মেরেছি আমরা, দেখবি বাবু? ইয়া চিতি।
সোৎসাহে আসন হতে উঠিয়া পড়িয়া অহীন্দ্র বলিল, কোথায়? কই? সঙ্গে সঙ্গে পরমোৎসাহে মাঝির দল আগাইয়া চলিল, সর্বাগ্রে ছেলেমেয়েরা যেন নাচিয়া চলিয়াছে। পল্লীর এক প্রান্তে এক বিশাল অজগর ক্ষতবিক্ষত দেহে মরিয়া তাল পাকাইয়া পড়িয়া আছে চিত্রিত মাংসস্তূপের মত। অহীন্দ্র ও রংলাল উভয়েই শিহরিয়া উঠিল। অহীন্দ্র প্রশ্ন করিল, কোথায় ছিল?
মাঝি পরম উৎসাহভরে বিকৃত ভাষায় বকিয়া গেল অনেক, সঙ্গে সঙ্গে হাত-পা নাড়িবার কি তাহার বিচিত্র ভঙ্গী! মোটমাট ঘটনাটা ঘটিয়াছিল এই–একটা নিতান্ত কচি ছাগল ছানা, আপনার মনেই নাকি লাফাইয়া বেনাবনের কোল ঘেঁষিয়া নাচিয়া ফিরিতেছিল। নিকটেই একজন মাঝি বসিয়া বাঁশী বাজাইতেছিল, আর কাছে ছিল তাহার কুকুর। কুকুরটা সহসা সভয়ে গর্জন করিয়া উঠিতেই মাঝি তাহার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া দেখিল, সর্বনাশ, সাপ বেনাবন হইতে হাতখানেক মুখ বাহির করিয়া নিমেষহীন লোলুপ দৃষ্টিতে দেখিতেছে ওই নর্তনরত ছাগশিশুটিকে। সাঁওতালের ছেলে বাঁশীটি রাখিয়া দিয়া তুলিয়া লইল ধনুক আর কাঁড় তীর। তারপর অব্যর্থ লক্ষ্যে সাপের মাথাটাই বিঁধিয়া দিল একেবারে মাটির সঙ্গে; তারপর চীৎকার করিয়া ডাকিল পাড়ার লোককে। তখন বিদ্ধমস্তক অজগর দীর্ঘ নমনীয় দেহ আছড়াইয়া ঘাসের বনে যেন তুফান তুলিয়া দিয়াছে। কিন্তু পাঁচ-সাতটা ধনুক হইতে সুতীক্ষ্ণ শরবর্ষণের মুখে সে বীর্য কতক্ষণ!
সাপ দেখিয়া ফিরিয়া আসিয়া বসিতেই একটি প্রৌঢ় সাঁওতাল-রমনী একটি বাটিতে সদ্যদোহা দুধ আনিয়া নামাইয়া দিল, দুধের উপর ফেনা তখনও ভাঙে নাই। মেয়েটি সম্ভ্রম করিয়া বলিল, বাবু তুমি খান।
অহীন্দ্র হাসিয়া ফেলিল। মাঝি বলিল, ই আমার মাঝিন বেটে বাবু! লে, গড় কর রাঙাবাবুকে– আমাদের রাঙাঠাকুরের লাতি।
রংলাল গালে হাত দিয়া কি ভাবিতেছিল, অকস্মাৎ আক্ষেপ করিয়া বলিয়া উঠিল, অ্যাঁ, একেই বলে ইঁদুরে গর্ত করে, সাপে ভোগ করে।
দুধের বাটিটা নামাইয়া দিয়া অহীন্দ্র বলিল, কেন?
ম্লান হাসি হাসিয়া রংলাল বলিল, কেন আবার, চর উঠল লদীতে, সাপখোপের ভয়ে কেউ ই-দিক আসত না। মাঝিরা এল, সাফ করছে, চাষ করছে; উ-দিকে জমিদার সাজছে লাঠি নিয়ে।–কি? না, চর আমাদের। আমরা যত সব চাষী-প্রজা বলছি, চর আমাদের। এর পর মাঝিদের তাড়িয়ে দিয়ে সবাই বসবে জেঁকে।
মাঝি তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, কেনে, আমরাও খাজনা দিব। তাড়াবে কেনে আমাদিগে?
রংলাল বলিল, তাই শুধো গা গিয়ে বাবুদিগে। আর খাজনা দিবি কাকে? সবাই বলবে, আমাকে দে ষোলআনা খাজনা।
কেনে, আমরা খাজনা দিব আমাদের রাঙাঠাকুরের লাতিকে- এই রাঙাবাবুকে।
অহীন্দ্র বলিল, না না মাঝি, চর যদি আমাদের না হয় তো আমাকে খাজনা দিলে হবে কেন? যার চর হবে, তাকেই খাজনা দেবে তোমরা।
তবে আমরা তুকেই খাজনা দিব, যাকে দিতে হয় তু দিস।
রংলাল হুঁশিয়ার লোক, প্রবীণ চাষী, ভূমিসংক্রান্ত আইন-কানুন সে অনেকটাই বোঝে, আর এও সে বোঝে যে, চরের উপর চক্রবর্তী-বাড়ির স্বত্ব যদি কোনরূপে সাব্যস্ত হয়, তবে অন্য বাড়ির মত অন্যায়-অবিচার হইবে না, তাহাদেরও অনেক আশা থাকিবে। অন্তত মায়ের কথার কখনও খেলাপ হয় না। সে অহীন্দ্রের গা টিপিয়া বলিল, বাবু ছেলেমানুষ, উনি জানেন না মাঝি। চর ওঁদেরই বটে।
মাঝি বলিল, আমরা সোবাই বলব, আমাদের রাঙাবাবুর চর।
কথাটা কিন্তু চাপা পড়িয়া গেল, সেই মেয়ে কয়টি যেমন ছুটিতে ছুটিতে গিয়াছিল, তেমনি ছুটিতে ছুটিতে ফিরিয়া আসিয়া রাঙাবাবুর সম্মুখে থমকিয়া দাঁড়াইল, তাহাদের সকলেরই কোঁচড়ভরা ওই ফুলের স্তবক। একে একে তাহারা আঁচল উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিল ফুলের রাশি। অতি সুমধুর গন্ধে স্থানটার বায়ুস্তর পর্যন্ত আমোদিত হইয়া উঠিল।
মাঝি একটি দীর্ঘাঙ্গী কিশোরীকে দেখাইয়া বলিল, এই দেহ্ রাঙাবাবু, ই আমার লাতিন বেটে! ওই যি আজ সাপ মেরেছে, উয়ার সাথে ইয়ার বিয়া হবে।
লজ্জাকুণ্ঠাহীন অসঙ্কোচ দৃষ্টিতে মেয়েটি তাহারই দিকে চাহিয়া ছিল, চাহিয়াই রহিল। অহীন্দ্র বলিল, আজ যাই মাঝি।
মেয়েরা সকলে মিলিয়া কলরব করিয়া কি বলিয়া উঠিল। মাঝি হাসিয়া বলিল, মেয়েগুলা বুলছে, উয়ারা নাচবে সব, তুকে দেখতে হবে।
কিন্তু সন্ধ্যে হয়ে গেল যে মাঝি।
মাঝি বলিল, মশাল জ্বেলে আমি তুকে কাঁধে করে রেখে আসব।
অহীন্দ্র আর ‘না’ বলিতে পারিল না। এমন সুন্দর ইহাদের নাচ, আর এত সুন্দর ইহাদের একটানা সুরের সুকণ্ঠের গান যে তাহা দেখিবার ও শুনিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না। সে বলিল, তবে একটু শিগগির মাঝি।
মেয়েরা সঙ্গে সঙ্গে কলরব করিতে করিতে ছুটিয়া চলিয়া গেল, সিরিং সিরিং অর্থাৎ গান গান। মরং বাবু রাঙাবাবু, অর্থাৎ তাদের মালিক রাজা রাঙাবাবু দেখিবেন।
মাদল বাজিতে লাগিল-ধিতাং ধিতাং, বাঁশের বাঁশীতে গানের সুর ধ্বনিত হইয়া উঠিল। অর্ধচন্দ্রাকারে রাঙাবাবুকে বেষ্টন করিয়া বসন্ত বাতাসে দোলার মত হিল্লোলিত দেহে দুলিয়া দুলিয়া নাচিতে আরম্ভ করিল সাঁওতাল তরুণীরা, সঙ্গে সঙ্গে বাঁশীর সুরের সঙ্গে সুর মিলাইয়া গান। বৃদ্ধ মাঝি বসিয়া ছিল অহীন্দ্রের পাশে, অহীন্দ্র তাহাকে প্রশ্ন করিল, গানে কি বলছে মাঝি?
বলছে উয়ারা, রাজার আমাদের বিয়া হবে; তাতেই রাণী সাজ ক’রে বসে আছে, রাজা তাকে লাল জবাফুল এনে দিবে।
পরক্ষণেই অশীতিপর বৃদ্ধ প্রায় লাফ দিয়া উঠিয়া একটি মাদল লইয়া বাদক পুরুষদের সঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া বাজাইতে আরম্ভ করিল।
রাত্রি প্রায় আটটার সময়, রায়বাবুদের কাছারীর সম্মুখ দিয়া কাহারা যাইতেছিল মশালের আলো জ্বালাইয়া। মশাল একালে একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার। ইন্দ্র রায় গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, কে যায়?
শুষ্ক বেনাঘাসের আঁটি বাঁধিয়া তাহাতে মহুয়ার তেল দিয়া মশাল জ্বালাইয়া বৃদ্ধ মাঝি তাহাদের রাঙাবাবুকে পৌঁছাইয়া দিতে চলিয়াছিল। সে উত্তর দিল, আমি বেটে, উ পারের চরের কমলা মাঝি।
বিস্মিত হইয়া রায় প্রশ্ন করিলেন, এত রাত্রে এমন আলো জ্বেলে কোথায় যাবি তোরা?
আমাদের রাঙাঠাকুরের লাতি মশায়, আমাদের রাঙাবাবুকে বাড়িতে দিতে যেছি গো!
রাঙাঠাকুর! সোমেশ্বর চক্রবর্তী! রায়ের মনে পড়ে গেল অতীতের কাহিনী।
.
০৪.
সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালিয়া লক্ষ্মীর ঘরে গৃহলক্ষ্মীর সিংহাসনের সম্মুখে পিলসূজের উপর প্রদীপটা রাখিয়া সুনীতি গলায় আঁচল জড়াইয়া প্রণাম করিলেন। গনগনে আগুন ভরিয়া ঝি ধূপদানি হাতে ঘরের বাহিরে দাঁড়াইয়া ছিল। ধূপদানিটি তাহার হাত হইতে লইয়া সুনীতি আগুনের উপর ধুপ ছিটাইয়া দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে ধুপগন্ধে ঘরখানি ভরিয়া উঠিল।
ঘরের দরজা বন্ধ করিতে করিতে সুনীতি বলিলেন, তুলসীমন্দিরে আর ঠাকুরবাড়িতে প্রদীপ আজ বামুনঠাকরুনকে দিতে বল্ মানদা। আমার বড্ড দেরি হয়ে গেল, বাবু হয়ত এখুনি রেগে উঠবেন।
তাড়াতাড়ি তিলের তেলের বোতলটি লইয়া তিনি উপরে রামেশ্বরের ঘরের দিকে চলিয়া গেলেন। রামেশ্বরের দরজা জানলা অহরহ বন্ধ থাকে, দিনরাত্রিই ঘরে একটা প্রদীপ জ্বলে, সে প্রদীপে পোড়ে তিলের তেল। উজ্জ্বল আলো তাঁহার চোখে একেবারে সহ্য হয় না। আলোর মধ্যে তিনি নাকি একেবারে দেখিতে পান না। অন্ধকারে বরং পান। তেলের বোতল হাতে সুনীতি সন্তর্পণে দরজা ঠেলিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন। প্রকাণ্ড বড় ঘরখানির মধ্যে ক্ষীণ শিখার একটি মাত্র প্রদীপের আলো জ্বলিতেছে। এত বড় ঘরের সর্বাংশে তাহার জ্যোতি প্রসারিত হইতে পারে নাই, চারি কোণের অন্ধকার অসীমের মত সীমাবদ্ধ জ্যোতির্মণ্ডলকে যেন ঘিরিয়া রহিয়াছে। আলো-অন্ধকারে সে যেন এক রহস্যলোকের সৃষ্টি করিয়াছে। তাহারই মধ্যে ঘরের মধ্যস্থলে সে আমলের প্রকাণ্ড পালঙ্কের উপর নিস্তব্ধ হইয়া রামেশ্বর বসিয়া আছেন।
ঘরের দরজা খুলিতেই রামেশ্বর অতি ধীরে মৃদুস্বরে প্রশ্ন করিলেন, সুনীতি?
ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিতে দিতে সুনীতি বলিলেন, হ্যাঁ আমি। তেল দিয়ে দিই প্রদীপে। জানলাগুলি খুলে দিই, সন্ধ্যে হয়ে গেছে।
দাও।
সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিলে ঘরের জানলা খোলা হয়। কখনও কখনও রামেশ্বর তখন খোলা জানলার ধারে দাঁড়াইয়া বহির্জগতের সহিত পরিচয় করেন। জানলা খুলিয়া দিতেই বন্ধ ঘরে বাহিরের বাতাস অপেক্ষাকৃত জোরেই প্রবেশ করিল। সঙ্গে সঙ্গে প্রদীপটি নিভিয়া গেল। রামেশ্বর বাহিরের নির্মল শীতল বাতাস বুক ভরিয়া নিঃশ্বাস লইয়া বলিলেন, আঃ!
সুনীতি বলিলেন, আলোটা নিবে গেল যে।
রামেশ্বর বলিলেন, বাতাসে চমৎকার ফুলের গন্ধ আসছে। এটা কি মাস বল তো?
চৈত্র মাস। তারপর চিন্তিতভাবে সুনীতি আবার বলিলেন, প্রদীপ তো এ বাতাসে থাকবে না।
রামেশ্বর বলিতেছেন, ‘ললিত-লবঙ্গ-লতা-পরিশীলন-কোমল-মলয়-সমীরে।
বাতি দিয়ে একটা শেজ জ্বেলে দেব?
শেজ?
হ্যাঁ, বাতির আলোও তো ঠাণ্ডা। এ বাতাসে প্রদীপ থাকবে না।
তাই দাও।– বলিয়া আবার আপন মনে আবৃত্তি করিলেন, মধুকরনিকর-করম্বিত-কোকিল-কূজিত কুঞ্জ-কুটীরে।
ঘরে শেজ ও বাতি ঠিক করাই থাকে, মধ্যে মধ্যে জ্বালিতে হয়। বাতাসের জন্যও হয়, আবার মধ্যে মধ্যে রামেশ্বরের ইচ্ছাও হয়। সুনীতি বাতি জ্বালিয়া, শেজের মধ্যে বসাইয়া দিলেন, তারপর কতকগুলি ধুপশলা জ্বালিয়া দিয়া বলিলেন, কাপড় ছাড়, সন্ধ্যের জায়গা ক’রে দিই।
হুঁ। করতে হবে বৈকি। না করলেই পাপ! করলে কিছুই না—কিচ্ছু না, কিচ্ছু না, কিচ্ছু না।
সুনীতি বাধা দিয়া বলিলেন, ও কি বলছ? রামেশ্বর মধ্যে মধ্যে এমনই করিয়া বকিতে আরম্ভ করেন, তখন বাধা দিতে হয়। অন্যথায় সেই একটা কথাই তিনি কিছুক্ষণ ধরিয়া এমনই করিয়া বকিয়া যান।
বাধা পাইয়া রামেশ্বর চুপ করিলেন। সুনীতি আবার বলিলেন, কাপড় ছাড়, সন্ধ্যে কর। আর অমন করে বকছ কেন?
না না না, আমি বকি নি তো। বকব কেন? কই, কাপড় দাও। রামেশ্বর অতি সন্তর্পণে বিছানা হইতে নামিয়া আসিলেন। স্বামীকে সন্ধ্যা করিতে বসাইয়া সিয়া সুনীতি বলিলেন, সন্ধ্যে করে ফেল আমি দুধ গরম করে নিয়ে আসি।
সুনীতি ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, রামেশ্বর সন্ধ্যে শেষ করিয়া জানলার ধারে দাঁড়াইয়া আছেন। সুনীতিকে দেখিবামাত্র তিনি বলিলেন, কি বাজছে বল তো?
দূরে ওই চরটার উপর তখন অহীন্দ্রকে ঘিরিয়া সাঁওতালেরা মাদল ও বাশী বাজাইতেছিল, মেয়েরা নাচিতেছিল-তাহারই শব্দ। সুনীতি বলিলেন সাঁওতালেরা মাদল বাজাচ্ছে।
বাঁশী শুনছ, বাঁশী?
হ্যাঁ। সন্ধ্যার সময় তো। মাঝিরা মাদল বাজাচ্ছে, বাঁশী বাজাচ্ছে, মেয়েরা নাচছে। ওদের ওই আনন্দ।
তুমি কবিরাজগোস্বামী শ্রীজয়দেবের গীতগোবিন্দ পড়েছ?
“করতলতালতরলবলয়াবলি-কলিত কলম্বন বংশে।
রাসরসে সহনৃত্যপরা হরিণা যুবতিঃ প্রশংসে”।
যমুনাপুলিনে বংশীধ্বনির সঙ্গে তাল দিয়ে গোপবালারাও একদিন নাচত। গীতগোবিন্দ তুমি পড় নি?
স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া সুনীতি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, তুমি কখনও পড়ে শোনাও নি, আমি নিজে তো সংস্কৃত জানি না।
আজ তোমাকে শোনাব, আমার মুখস্থ আছে।
বেশ, এখন দুধটা খেয়ে নাও দেখি! বলিয়া সম্মুখে দুধের বাটি আগাইয়া দিলেন। পান করিয়া বাটি সুনীতির হাতে দিতেই সুনীতি জলের গ্লাস ও গামছা স্বামীর সম্মুখে ধরিলেন। হাতমুখ ধুইয়া রামেশ্বর আবার বলিলেন, কবিরাজগোস্বামী বলেছেন কি জান?
“যদি হরি-স্মরণে সরসং মনো যদি বিলাস কলাসূ কুতূহলং।
মধুর কোমল কান্ত পদাবলীং শৃণু তদা জয়দেব সরস্বতীম্।”
শোনাব, তোমাকে আজ শোনাব।
আনন্দে সুনীতির বুকখানা যেন ভরিয়া উঠিল, তিনি বলিলেন, তাহলে তাড়াতাড়ি আমি কাজগুলো সেরে আসি। পরমুহর্তেই আবার যেন স্তিমিত হইয়া গেলেন– কতক্ষণ, এ রূপ কতক্ষণের জন্য?
হ্যাঁ, এস। বাতাস আজ বড় মিষ্টি বইছে। বসন্তকাল কিনা। আচ্ছা সুনীতি, দোল পূর্ণিমা চলে গেছে?
হ্যাঁ। আজ কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমী।
কই, আমাকে তো আবীর দিলে না?
সুনীতি অপরাধীর মত নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।
এনো, এনো, আবীর থাকে তো নিয়ে এস এক মুঠো আজ।
সুনীতি এ কথারও উত্তর দিলেন না, শুধু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন।
আর শোন। জয়দেব সরস্বতীর পদাবলী যদি শুনবে, তবে অতি সুন্দর একখানি কাপড় পরবে। সুন্দর করে বেণী রচনা করবে। তার পর রসরাজের মূর্তি হৃদয়ে স্মরণ করে লীলাবিভোর মন নিয়ে শুনতে হবে।
সুনীতি ভাল করিয়া জানেন যে, ফিরিয়া আসিতে আসিতে স্বামীর এ রূপ আর থাকিবে না। কিন্তু তিনি কখনও স্বামীর কথার প্রতিবাদ করেন না, ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন, তাই আসব।
চুলটা যেন বেঁধে ফেলো।
বাঁধব।
হ্যাঁ। ঘরে আতর নেই–আতর
আছে, তাও আনব।
আমায় এখুনি একটু দিতে পার?
দিচ্ছি। সুনীতি সঙ্গে সঙ্গে বাক্স খুলিয়া একটি সুদৃশ্য আতরদান বাহির করিলেন। তুলায় আতর মাখাইয়া স্বামীর হাতে দিয়া ঘর হইতে বাহির হইবার জন্য ফিরিলেন। কিন্তু রামেশ্বর ডাকিলেন, শোন।
সুনীতি বলিলেন, বল।
ওই আলোর সম্মুখে তুমি একবার দাঁড়াও তো। অন্ধকারের মধ্যে আমার বাস, অনেক দিন তোমাকে যেন আমি ভাল করে দেখিনি।
সুনীতি স্থিরভাবে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইলেন। রামেশ্বর একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, দৃষ্টি যাওয়ার চেয়ে মানুষের বড় দুঃখ আর নেই। ভীষণ পাপে, অভিসম্পাত না হ’লে মানুষের চোখ যায় না।
সুনীতি ব্যথিত কণ্ঠে বলিলেন, কিন্তু চোখ তো তোমার খারাপ হয় নি, তিন-চার বার ডাক্তার দেখানো হ’ল, তাঁরা তো তা বলেন না।
তারস্বরে প্রতিবাদ করিয়া রামেশ্বর বলিলেন, জানে না, তারা কিছুই জানে না, তুমিও জান না। দিনের আলোর মধ্যে চোখ আমার আপনি বন্ধ হয়ে যায়, কে যেন ধরে চোখে ছুঁচ ফুটিয়ে দেয়। নিবিয়ে দাও সুনীতি, ও আলোটা নিবিয়ে দাও, নয় আড়ালে সরিয়ে দাও। আঃ।
আলোটা অন্তরালে সরাইয়া দিয়া সুনীতি নীরবে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।
.
সে আমলের চকমিলানো বাড়ি, নীচের তলায় চারিদিকেই ঘর, একেবারে অবরুদ্ধ বলিলেই হয়। বাহিরের এমন মিষ্ট বাতাস, অথচ এ-বাড়ির নীচের তলায় বেশ গরম পড়িয়া গিয়াছে। স্বামীর জন্য খাবার সুনীতি নিজের হাতেই প্রস্তুত করেন, খাবার প্রস্তুত করিতে করিতে তিনি ঘামিয়া যেন স্নান করিয়া উঠিলেন।
পাচিকা বলিল, ওরে বাপ রে, মা যেন ঘেমে নেয়ে উঠলেন একেবারে! আমি যে এতক্ষণ আগুনের আঁচে রয়েছি, আমি তো এত ঘামি নি!
মানদা ঝি বলিল, পাখাটা নিয়ে আসি আমি।
অত্যন্ত লজ্জিত এবং কুণ্ঠিতভাবে সুনীতি বলিলেন, না রে, না, থাক। এই তো হয়ে গেছে আমার। এমন ভাবে ঘামিয়া ওঠাটা তাঁদের কাছেও অত্যন্ত অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হইতে ছিল। তাঁহার খাবার তৈয়ারিও শেষ হইয়াছিল, তিনি খাবারগুলি গুছাইয়া উঠিয়া পড়িলেন। খাবার রাখিয়া দিয়া বলিলেন, দু বালতি জল তুলে দে তো মানদা, গা ধুয়ে ফেলি একটু।
মানদা পুরানো ঝি, সে বলিল, এই যে সন্ধ্যায় গা ধুলেন মা। আবার গা ধোবেন কি গো, এই দো-রসার সময়? ভিজে গামছা দিয়ে গা মুছে ফেলুন বরং
না রে, সমস্ত শরীর যেন ঘিনঘিন করছে আমার। তার পর ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, আমার কি কখনও মরণ হয় রে মানী, তাহ’লে সংসারে ভুগবে কে?
মানদা আর কথা না বলিয়া তাড়াতাড়ি জল তুলিয়া গামছা আনিয়া সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক করিয়া দিল। আপনার হাত দুইখানি নাকের কাছে আনিয়া শুকিয়া সুনীতি বলিলেন, নাঃ, ধোঁয়ার গন্ধ, সাবান না দিলে যাবে না। তুই কার কাছে ঘুঁটে নিস মানদা? ঘুঁটে ভিজে থাকে।
বলিতে বলিতে তিনি ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া সাবান বাহির করিয়া লইয়াও চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তোলা কাপড় একখানা বাহির করিলে হয়, কিন্তু। আবার তিনি এক গা ঘামিয়া উঠিলেন। মনের মধ্যে একটা দারুণ সঙ্কোচ তাঁহাকে পীড়িত করিতেছিল।
মানদা ডাকিল, মা আসুন।
সুনীতি তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া হাসিয়া বলিলেন, বাক্স খুলে দেখলাম, কাপড়গুলো সব পুরনো হয়ে যাচ্ছে। ভাবলাম, কি হবে রেখে, পরে ফেলি। কিন্তু তোরা হাসবি ব’লে আর পারলাম না।
মানদা ও পাচিকা একসঙ্গে দুইজনেই হাঁ-হাঁ করিয়া উঠিল, না মা, না, আপনি পরুন, একটু ভাল কাপড় পরলে আপনাকে যা সুন্দর লাগে দেখতে। পরুন মা পরুন।
পরব?
হ্যাঁ মা পরুন, পরবেন বৈকি।
বুড়ো মেয়ের শখ দেখে তোরা হাসবি তো?
হেই মা, তাই হাসতে পারি? আর আপনি বুড়ো হলেন কি করে মা? বড় দাদাবাবু এই আঠারোতে পড়লেন; আমি তো জানি, আপনার পনেরো বছরে দাদাবাবু কোলে আসে। তা হ’লে কত হয়-এই তো মোটে তেত্রিশ বছর বয়েস আপনার।
সুনীতির সকল সঙ্কোচ কাটিয়া গেল। তিনি আবার বাক্স খুলিয়া বাছিয়া একখানি ঢাকাই শাড়ি বাহির করিয়া আনিলেন। গা ধুইতে ধুইতে বলিলেন, গরমের দিন এল, আর আমার এই চুলের বোঝা নিয়ে হ’ল মরণ।
মানদা বলিল, উঠুন আপনি গা ধুয়ে, আপনার চুলটা বেঁধে দেব আজ। চুল বাঁধতে বললেই আপনি বলেন, ছেলে বড় হয়েছে, বুড়ো হয়েছি, কত কি। দেখুন গিয়ে ছোট তরফের রায়গিন্নীকে, আপনার চেয়ে কত বড়, চুলে পাক ধরেছে, তবু রোজ চুল বাঁধবেন।
হাত মুখে সাবান দিয়ে গা ধোয়া শেষ করিয়া সুনীতি বলিলেন, দে তাই, চুলগুলো বিনুনি ক’রে দে তো। এলোচুল খুলে পিঠে পড়ে এমন সুড়সুড় করে পিঠ!
সুনীতির চুলগুলো ভ্রমরের মত কালো আর কোঁকড়ানো। হাতের মুঠিতে চুলগুলি ধরিয়া মানদা বলিল, বাহারের চুল বটে মা। আ-হা-হা, কি নরম! ছোট দাদাবাবু ঠিক তোমার মত দেখতে, কিন্তু চুলগুলিনও পায় নাই, এমন বাহারের চোখও পায় নাই।
সুনীতি চমকিয়া উঠিলেন, কই, অহীন্দ্র তো এখনও ফিরল না? তিনি উৎকণ্ঠিত স্বরে বলিলেন, তাই তো রে, অহি তো এখনও ফিরল না? বেরিয়েছে, সেই কখন?
মানদা বলিল, বেশ, দেখুন গিয়ে তিনি বসে বসে রংলাল মোড়লের সঙ্গে গল্প করছেন। আমি দেখে এসেছি তাঁদের দুজনকে জল আনতে গিয়ে নদীর ধারে। মোড়ল একবার এই হাত ছুঁড়ছে, একবার ওই হাত ছুঁড়ছে যেন বক্তৃতা করছে।
সুনীতি বলিলেন, ওই ওর এক নেশা। যত চাষীভূষির সঙ্গে বসে গল্প করবে। রায়েরা নিন্দে করে, মহী তো আমার ওপরেই তাল ঝাড়বে। তবু তো বাবুর কানে ওঠে না।
মানদা বলিল, রায়েদের কথা ছাড়ান দেন মা, ওরা এ-বাড়ির নিন্দে পেলে আর কিছু চায় না। আর ছোট দাদাবাবুর মত ছেলে তোমার হাজারে একটা নাই। আমি তো দেখি নাই! দেখে এস গিয়ে রায়বাড়ির ছেলেদিগে, কথা কি সব, যেন ছূঁচ বিঁধছে। তুই-তোকারি, চোপরাও, হারামজাদা-হারামজাদী তো ঠোঁতে লেগে আছে।–নেন মা, এইবার সিঁথিতে সিঁদুর নেন। কপালেও নেবেন, নিতে হয়।
সুনীতি স্থিরদৃষ্টিতে পশ্চিম দিকে একতলার ছাদের উপর দিয়া ওপারের শূণ্যমণ্ডলের দিকে চাহিয়া ছিলেন। ওপাশে কাছারি-বাড়ির প্রাঙ্গণে এত আলো কিসের? শূণ্যমণ্ডলটা পর্যন্ত আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে। তিনি শঙ্কিত হইয়া বলিলেন, দেখ তো বেরিয়ে মানদা, বাইরে এত আলো কিসের?
মানদা সশঙ্কচিত্তে সন্তর্পণে বাহির হইয়া গিয়া কিছুক্ষণ পরেই ছুটিয়া ফিরিয়া আসিল।–ওগো মা, একদল সাঁওতাল, এ-ই সব মশাল জ্বেলে দাদাবাবুকে পৌঁছে দিতে এসেছে। এই সব ঠকাঠক পেনাম করছে। দাদাবাবুকে বলছে ‘রাঙাবাবু’।
রাঙাবাবু! সুনীতি শিহরিয়া উঠিলেন। সাঁওতালদের রাঙাঠাকুর-তাঁহার শ্বশুরের কাহিনী তিনি বহুবার শুনিয়াছেন। পরক্ষণেই আবার তাঁহার মন তাঁহার শ্বশুরকুলের গৌরবে ভরিয়া উঠিল। আর ওই আদিম বর্বর মানুষদের সকৃতজ্ঞ আনুগত্যের কথা স্মরণ করিয়া তাহাদের প্রতিও মমতার সীমা রহিল না। এ-বাড়িকে সাঁওতালরা কোনদিন ভোলে নাই, সরকারের সহিত মকদ্দমার পর হইতে এই বাড়িই সযত্নে সাঁওতালদের সহিত
সংস্রব পরিহার করিয়া চলিয়াছে। বহু দিন ধরিয়া সরকার-পক্ষ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন তাঁহার স্বামীর উপর।
হাসিতে হাসিতে বাড়িতে প্রবেশ করিল অহীন্দ্র, তাহার পিছনে পিছনে রংলাল আসিয়া বাড়ির দরজায় দাঁড়াইল।
আজ ওই চরটা দেখে এলাম মা। সাঁওতালেরা যা খাতির করল। আমার নাম দিয়েছে রাঙাবাবু। একটা যা অজগর চিতি ওরা মেরেছে-প্রকাণ্ড বড়। অহীন্দ্রের ইচ্ছা হইতেছিল, একেবারে সকল কথা এক মুহূর্তে সব জানাইয়া দেয়।
মা বলিলেন, ওই সাপখোপ-ভরা চর, ওখানে তুমি কেন গিয়েছিলে?
অহীন্দ্র হাসিয়া বলিল, ‘সাত কোটি সন্তানের হে মুগ্ধ জননী, রেখেছ বাঙালী করে, মানুষ করনি’। গেলাম তো হ’ল কি? ভয় কিসের?
বাহির-দরজায় রংলাল দাঁড়াইয়া ছিল, সে ডাকিল, দাদাবাবু! তাহার গামছায় ছিল সেই ফুলগুলি।
সুনীতি চকিত হইয়া মাথায় ঘোমটা টানিয়া দিয়া বলিলেন, মাঝিরা চলে গেল নাকি? মানদা দাঁড়াতে বল্ তো মাঝিদের। মুড়কি আর নাড়ু দিতে হবে ওদের।
রংলাল বলিল, ওগো মানদা, এইগুলো বরং নাও তুমি, আমি যাই মাঝিদের আটক করি। যে বোঙা জাত, হয়ত তোমার কথাই বুঝবেই না।
মানদা ফুলগুলি আনিয়া ঢালিয়া দিয়া বলিল, তাই বলি, দাদাবাবু এলেন আর এমন গন্ধ কোথা থেকে উঠল! আহা-হা, এ কি ফুল গো? কি ফুল দাদাবাবু?
ফুলের গন্ধ ও কদম্বফুলের মত পুস্পগুচছগুলির গঠন-ভঙ্গি দেখিয়া সুনীতিও আকৃষ্ট হইলেন, তিনিও কয়েকটি পুস্পগুচ্ছ তুলিয়া লইয়া বলিলেন, ভারী সুন্দর ফুল তো?
উচ্ছ্বসিত হইয়া অহীন্দ্র বলিল, ওই ফুলের গন্ধেই তো চরের ভেতর গেলাম। রংলাল বললে, মাঝিরা ঠিক সন্ধান জানে! গেলাম যদি তো, আমাকে দেখেই কমল মাঝি, ওদের মোড়ল- উঃ, কি চেহারা তার মা, ঠিক যেন একটা পাহাড়ের মত-আমাকে দেখেই ঠিক চিনে ফেললে, বললে, হুঁ, ঠিক তেমনি পারা, তেমনি আগুনের মত রঙ, তেমনি চোখ, তেমনি চুল; ঠিক আমাদের রাঙাঠাকুরের লাতি! সেখানে মেয়েরা সব গোছায় গোছায় এই ফুল খোঁপায় পরে আছে। সেই মেয়েরা এনে দিলে এত ফুল। সবাই নিয়ে এল এক এক আঁচল ভরে। যার না নিই, সেই রাগ করে। রংলাল বললে, সবারই নোব দাদাবাবু, চলুন আমি নিয়ে যাচ্ছি।
সুনীতি বলিলেন, যা তুই কতকগুলো নিয়ে বাবুর ঘরে দিয়ে আয়। ভারী খুশি হবেন উনি। শুনেছিস তো, উনি নাকি সেকালে রোজ সন্ধ্যেতে ফুলের মালা পরতেন। যা নিয়ে যা।
অহীন্দ্র বলিল, না, তুমি গিয়ে দিয়ে এস।
সে কি? এবার এসে একবারও তো তুই বাবুর সঙ্গে দেখা করিস নি। না না, এ তো ভাল নয় অহি।
আমার বড় কষ্ট হয় মা। তিনি কেমন হয়ে গেছেন। অথচ এত বড় পণ্ডিত, কি সুন্দর সংস্কৃত বলেন! আমার কান্না পায়।
সুনীতির চোখ ছলছল করিয়া উঠিল। তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া নিজেই ফুল লইয়া উঠিলেন। বলিলেন, কি করব বল, তোদের অদৃষ্ট আর আমার পোড়া কপাল! আচ্ছা, আমিই দিয়ে আসছি। যাইতে যাইতে আবার ফিরিয়া আসিয়া বসিলেন, ওগো বামুন-মেয়ে, মাঝিদের মুড়কি আর নাড়ু দিও সকলকে।
এতক্ষণে অহীন্দ্র মাকে দেখিয়া বলিল, বাঃ, বড় সুন্দর লাগছে মা তোমাকে আজ! অথচ কেন তুমি চব্বিশ ঘণ্টা এমন গরিব-গরিব সেজে থাক?
সুনীতি লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিলেন, তবু চট করিয়া আপন লজ্জা ঢাকিয়া বলিলেন, আজ আমি রাঙাবাবুর মা হয়েছি কিনা, তাই। আর বেয়াই আসবে বলে সেজেছি এমন, তোর সাঁওতালদের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেব।
ছেলে লজ্জিত হইয়া পড়িল, মাও দ্রুতপদে উপরে উঠিয়া গেলেন। অতি অল্পক্ষণ পরেই মাঝিদের লইয়া রংলাল আসিয়া অন্দরের বহিদ্বারে দাঁড়াইয়া ডাকিল, দাদাবাবু!
মানদা বলিল, এস মোড়ল, ভেতরে নিয়ে এস ওদের, মা ওপরে আছেন।
সুনীতি দরজা ঠেলিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, ঘর অন্ধকার, বাতিটা বোধ হয় নিভিয়া গিয়াছে। তিনি দরজাটা আবার খুলিয়া অহিকে লক্ষ্য করিয়া বলেলেন, একটা প্রদীপ নিয়ে আয় তো অহি।
অন্ধকার কক্ষের মধ্য হইতে রামেশ্বর বলিলেন, কে, সুনীতি? তাহার কণ্ঠস্বর অত্যন্ত উত্তেজিত এবং মৃদু চাপা ভঙ্গির মধ্যে আশঙ্কার আভাস সুপরিস্ফুট।
সুনীতি বুঝিলেন, আলো নিভিয়া যাওয়ায় রামেশ্বর উত্তেজিত হইয়াছেন। চোখে তাঁহার আলো সহ্য হয় না, কিন্তু গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে একা থাকিতেও তিনি আতঙ্কিত হইয়া ওঠেন। সুনীতি বলিলেন, এই এক্ষুনি আলো নিয়ে আসছে। কিন্তু আমি কি এনেছি বল তো? খুব একটা মিষ্টি গন্ধ পাচ্ছ?
সুনীতির কথার উত্তর তিনি দেলেন না, উত্তেজিতভাবেই তেমনি চাপা গলায় বলিলেন, এত আলো কেন কাছারি-বাড়িতে সুনীতি? এত লোক? আমাকে কি ওরা ধরে নিয়ে যাবে? তাই আলোটা নিবিয়ে দিয়েছি।
সুনীতির সকল আনন্দ ম্লান হইয়া গেল, তিনি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, না না। ওরা সব সাঁওতাল, অহিকে পৌঁছে দিতে এসেছিল।
অহিকে পৌঁছে দিতে এসেছিল? সাঁওতাল?
হ্যাঁ, কালীর ওপারে যে চরটা উঠেছে, অহি আজ সেই চরে বেড়াতে গিয়েছিল। সেখানে সাঁওতালেরা এসে বাস করছে; রাত্রি হ’তে তারা সব মশাল জ্বেলে অহিকে পৌঁছে দিয়ে গেল। অহি তোমার জন্য খুব চমৎকার ফুল এনেছে, গন্ধ পাচ্ছ না?
ফুল? তাই তো, চমৎকার গন্ধ উঠেছে তো! অহি এনেছে? আমার জন্য?
হ্যাঁ।
অহি আলো লইয়া দরজা ঠেলিয়া প্রবেশ করিল। সুনীতি আলোর ছটায় ফুলের স্তবকটি রামেশ্বরের সম্মুখে ধরিলেন। রামেশ্বর মুগ্ধদৃষ্টিতে দেখিতে দেখিতে বলিলেন, কুটজ কুসুম। বনবালারা, পর্বতদুহিতারা সেকালে কানে চুলে আভরণস্বরূপ ব্যবহার করতেন। আমরা বলি কুর্চি ফুল।
অহি বলিয়া উঠিল, সাঁওতালদের মেয়েরা দেখলাম থরে থরে সাজিয়ে খোঁপায় পরেছে।
সুনীতি বলিলেন, অহিকে নাকি সাঁওতালরা দেবতার মত খাতির করেছে, শ্বশুরের নাম ক’রে বলেছে, তুই বাবু আমাদের রাঙাঠাকুরের নাতি, দেখতেও ঠিক তেমনি। এক বুড়ো সাঁওতাল তাঁকে দেখেছিল, সে বলেছে, অহি নাকি ঠিক আমার শ্বশুরের মত দেখতে। ওর নাম দিয়েছে রাঙাবাবু।
রামেশ্বর স্তব্ধ হইয়া অহির মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, তোল তো, আলোটা তোল তো সুনীতি, দেখি।
সুনীতি আলো তুলিয়া অহীন্দ্রের মুখের পাশে ধরিলেন। দেখিতে দেখিতে সম্মতিসূচক ভঙ্গিতে ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে তিনি বলিলেন, হুঁ। কণ্ঠস্বরে একটি সকরুণ বিষণ্ণ সুর সুনীতি ও অহীন্দ্র দুজনকেই স্পর্শ করিল। হয়ত কোনও অবান্তর অসম্ভব কথা এইবার তিনি বলিয়া উঠিবেন আশঙ্কা করিয়া সুনীতি বলিলেন, অহি, যা বাবা, তুই খেয়ে নিগে। আমি আলোটা জ্বেলে দিয়ে আসছি।
অহি চলিয়া গেল। সুনীতি আলোটা জ্বালিয়া দিয়া একটি শ্বেতপাথরের গ্লাসে ফুলগুলি সাজাইয়া দিয়া বলিলেন, এই দেখ, খুব সুন্দর কাপড় পরেছি আজ, চুলও বেঁধেছি; গীতগোবিন্দ শোনাবে তো?
রামেশ্বরের কানে সে কথা প্রবেশই করিল না, তিনি যেন কোন গভীর চিন্তার মধ্যে আত্মহারার মত মগ্ন হইয়া গিয়াছেন। সুনীতি তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া ডাকিয়া বলিলেন, কি ভাবছ?
ভাবছি, অহি যদি সাঁওতালদের নিয়ে গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে হাঙ্গামা করে!
না না, অহি সে-রকম ছেলে নয়; খুব ভাল ছেলে, প্রত্যেকবার স্কুলে ফার্স্ট হয়। তুমি তো ডেকে কথাবার্তা বল না; কথা বলে দেখো, ভাল সংস্কৃত শিখেছে, কত দেশ-বিদেশের গল্প বলে!
রামেশ্বরের দুর্ভাবনা ইহাতেও গেল না, তিনি বার বার ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, সাঁওতালেরা চিনেছে যে! আবার নাম দিয়েছে বলছ- রাঙাবাবু, আর ঠিক সেই রকম দেখতে!
সুনীতির এক এক সময় ইচ্ছা হয়, কঠিন একটা পাথরের নিষ্ঠুর আঘাতে আপনার কপালখানাকে ভাঙিয়া ললাটলিপিকে ধুলার মধ্যে বিলুপ্ত করিয়া দেন। তিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া চলিয়া আসিলেন। নীচে মানদা ও বামুন-ঠাকুরন বসিয়া সাঁওতালদের কথা আলোচনা করিতেছিল, মানদা বলিতেছিল, আমার সবচেয়ে ভাল লাগে ওদের বাঁশী। শুনছ, বাড়ি ফিরতে ফিরতে বাঁশী বাজাচ্ছে, শুনতে পাচ্ছ?
সুনীতি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, এখনও তোমাদের গল্প হচ্ছে মা? ছি!
.
০৫.
অতি প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করা ইন্দ্র রায়ের চিরদিনের অভ্যাস। এককালে ভোরে উঠিয়া বাহিরে আসিয়া নিয়মিত ব্যায়াম করিতেন। বয়েসের সঙ্গে ব্যায়ামের অভ্যাস আর নাই, কিন্তু এখনও তিনি শয্যা পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়া নিয়মিত খানিকটা হাঁটিয়া আসেন।
একলাই যাইতেন। গ্রামের উত্তরে লাল মাটির পাথুরে টিলা, অবাধ প্রান্তর। ক্রোশ কয়েক দূরে একটা শাল-জঙ্গল, শাল-জঙ্গলের গায়েই একটা পাহাড়, সাঁওতাল পরগণার পাহাড়ের একটা প্রান্ত আসিয়া এ অঞ্চলেই শেষ হইয়াছে। ওই টিলাটাই ছিল তাঁহার প্রাতভ্রমণের নির্দিষ্ট স্থান, পৃথিবীর কক্ষপথের মত প্রাতভ্রমণের নির্দিষ্ট কক্ষপথ। সম্প্রতি তাহার একজন সঙ্গী জুটিয়াছে। তাঁহারই সমবয়সী এক বিদেশী ভদ্রলোক, ডিসপেপসিয়ায় মৃতপ্রায় হইয়া স্বাস্থ্যকর স্থানের সন্ধানে এখানেই আসিয়া পড়েন, ইন্দ্র রায়ের আশ্রয়ে। ইন্দ্র রায় বর্তমানে বাড়ি-ঘর ও কিছু জমিজায়গা দিয়া তাঁহাকে এখানেই বাস করাইয়াছেন। প্রাতভ্রমণের পথে ইন্দ্র রায়ের সঙ্গী হন এই ভদ্রলোক।
আজ ইন্দ্র রায় বাহিরে আসিয়া বাড়ির ফটক খুলিয়া বাহির হইতে গিয়া আবার ফিরিলেন। হিন্দুস্থানী বরকন্দাজ মুচকুন্দ সিং কাছারির বারান্দায় চিত হইয়া পড়িয়া অভ্যাসমত নাক ডাকাইতেছিল, রায় তাহার স্থূল উদরের উপর হাতের ছড়িটার প্রান্ত দিয়া ঠেলিয়া ডাকিলেন, এই, উঠো জলদি উঠো।
সিং নড়িল না, নিদ্রারক্ত চোখ দুইটা বিস্ফারিত করিয়া দেখিল, লোকটা কে? রায়কে দেখিয়া তাহার সমস্ত দেহটা নড়িয়া উঠিল চমকানোর ভঙ্গিতে, পরমুহূর্তে সে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, হুজুর!
এস আমার সঙ্গে, লাঠি নাও।
চাপরাস, আওর পাগড়ি?
ধমক দিয়া রায় বলিলেন, না, এমনি লাঠি নিয়ে এস, তা হ’লেই হবে।
লাঠি লইয়া সিং খুঁজিতেছিল, আঃ, তেরি আঙ্গোছা কাঁহা গইল বা? অন্তত গামছাটা কাঁধে না ফেলিয়া যাইতে কোনমতেই তাহার মন উঠিতেছিল না। গামছাটা কোনমতে বাহির করিয়া সেখানাই মাথায় জড়াইয়া লইয়া মুচকুন্দ বাহির হইল।
রায়ের সঙ্গী অচিন্ত্যবাবু ততক্ষণে উঠিয়া আপনার মেটে ঘরের দাওয়ায় বসিয়া নিবিষ্ট মনে চোখের তারা দুইটি গোঁফের উপর আবদ্ধ করিয়া বোধ হয় কাঁচা চুল বাছিতেছিলেন।
রায় আসিয়া দাঁড়াইতেই তিনি বলিলেন, কাঁচা গোঁফ আর নাই বললেই চলে রায় মশায়।
রায় হাসিয়া বলিলেন, সেটা তো আয়নাতেই দেখতে পান অচিন্ত্যবাবু।
অচিন্ত্যবাবু ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, উঁহু, আয়না আমি দেখি না।
রায় আশ্চর্য হইয়া গেলেন, আয়না দেখেন না? কেন?
ও দেখলেই আমার মনে হয়, শরীরটা ভয়ঙ্কর খারাপ হয়ে গেছে মনে হয়, আর বেশী দিন বাঁচব না। কিন্তু আজ আপনার সঙ্গে বাহন কেন?
আজ একটু দিগন্তরে যাব; নদীর ওপারে একটা চর উঠেছে সেই দিকে যাব।
অচিন্ত্য চমকিয়া উঠিলেন, ওরে বাপ রে! ওখানে শুনেছি ভীষণ সাপ মশায়। শেষকালে কি প্রাণ হারাবেন? না না, ও মতলব ছাড়ুন, চর-ফর দেখতে ওই বরকন্দাজ-ফরকন্দাজ কাউকে ভেজে দেন, না হয় নায়েব-গোমস্তা।
আরে না না, ভয় নেই আপনার। ওখানে এখন সাঁওতাল এসে রয়েছে, রীতিমত রাস্তা করেছে, চাষ করছে, কুয়ো খুঁড়েছে, কুয়োর জল নাকি খুব উৎকৃষ্ট। নদীর জলটাই আবার ফিল্টার হয়ে যায় তো। চলুন, চাষের জায়গা কি রকম দেখবেন, আপনার তো অনেক রকম প্ল্যানট্যান আছে, চলুন কোনটা যদি কাজে লাগানো যায় তো দেখা যাক।
অচিন্ত্যবাবু আর আপত্তি করিলেন না, কিন্তু গতি তাঁহার অতি মন্থর হইয়া পড়িল। ভদ্রলোকের বাপ ছিলেন দারোগা, নিজে এফ.এ. পাস করিয়া চাকরি পাইয়াছিলেন পোস্ট অফিসে। কিন্তু রোগের জন্য অকালে ইনভ্যালিড পেনশন লইয়াছেন। সামান্য পেনশনে সংসার চলিয়া যায়; পিতার ও নিজের চাকরি-জীবনের সঞ্চয় লইয়া নানা ব্যবসায়ের কথা ভাবেন, সে সম্বন্ধে খোঁজখবর লইয়া কাগজে-কলমে লাভ লোকসান করিয়া ফেলেন, কিন্তু প্রত্যক্ষ কর্মের সময় হাত-পা গুটাইয়া বসেন। পুনরায় অন্য ব্যবসায়ের কথা চিন্তা করিতে আরম্ভ করেন।
কালীন্দির কূলে আসিয়া অচিন্ত্যবাবু বলিলেন, বিউটিফুল সানরাইজ! আপনি বরং ঘুরে আসুন রায় মশায়, আমি বসে বসে সূর্যোদয় দেখি।
রায় মৃদু হাসিয়া বলিলেন, যাবেন না? কিন্তু ভয় কি মৃত্যুর গতি রোধ করতে পারে অচিন্ত্যবাবু?
অচিন্ত্যবাবু ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, তবু যথাসাধ্য সে ভাব গোপন করিয়া বলিলেন, তা বলে বিপদের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়ার নাম বাহাদুরি নয়! ধরুন, পাঁচ হাজার টাকার তোড়ার পাশে একটা জীবন্ত সাপ রেখে দিয়ে যদি কেউ বলে, নিয়ে যেতে পারলে টাকাটা তোমার; যাবেন আপনি নিতে?
রায় এবার হা-হা করে হাসিয়া বলিলেন, নিশ্চয়। সাপটাকে মেরে টাকাটা নিয়ে নেব। অচিন্ত্যবাবু সবিস্ময়ে রায়ের মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, তা আপনি নিন গিয়ে মশাই, ও আমি নিতেও চাই না, যেতেও চাই না। কথা শেষ করিয়াই তিনি নদীর ঘাটে শ্যামল ঘাসের উপর বসিয়া পড়িলেন। বলিলেন, এই হ’ল ঠিক আলট্রাভায়োলেট রে- জবাকুসুমসঙ্কাশ।
ইন্দ্র রায় হাসিয়া জুতা খুলিয়া নদীর জলে নামিলেন।
আসল কথা, ইন্দ্র রায় বিগত সন্ধ্যায় সেই মশালের আলো জ্বালিয়া সাঁওতালবেষ্টিত রাঙাঠাকুরের পৌত্রের ওই শোভাযাত্রা নিতান্ত সাধারণভাবে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। রাঙাঠাকুরের নাতি-আমাদের রাঙাবাবু, কথাটার মধ্যে একটা বিশেষ অর্থের সন্ধান যেন তিনি পাইয়াছিলেন। রাত্রির শেষ প্রহর পর্যন্ত তিনি বসিয়া বসিয়া এই কথাটাই শুধু চিন্তা করিয়াছিলেন। একটা দুগ্ধপোষ্য বালক এক মুহূর্তে হিমালয়ের মত অলঙ্ঘ্য হইয়া উঠিল যে! সাঁওতাল জাতের প্রকৃতি তো তাহার অজানা নয়! আদিম বর্বর যাহাকে দেবতা বলিল, তাহাকে কখনও পাথর বলিবে না। বলুক, রামেশ্বরের ওই সুকুমার ছেলেটিকে দেবতা তাহারা বলুক, কিন্তু দেবতাটি ওই চর প্রসঙ্গে কোন দৈববাণী করিয়াছে কি না সেইটুকুই তাঁহার জানার প্রয়োজন। আসলে সেইটুকুই আশঙ্কার কথা। সেই কথাই জানিতে তিনি আজ দিক-পরিবর্তন করিয়া চরের দিকে আসিয়াছেন।
চরের ভিতর সাঁওতালপল্লীর প্রবেশমুখেই দাঁড়াইয়া তিনি মুচকুন্দ সিংকে বলিলেন, ডাক তো মাঝিদের।
মুচকুন্দ সিং পল্লীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার মোটা গলায় হাঁকে-ডাকে সোরগোল বাধাইয়া তুলিল। তাহার নিজের প্রয়োজন ছিল একটু চুন ও খানিক তামাক পাতার। তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিবার সময় ওটা ভুল হইয়া গিয়াছে। পল্লীর মধ্যে পুরুষেরা কেহ নাই, তারা সকলেই আপন আপন গরু মহিষ ছাগল এই বন জঙ্গলের মধ্যেই কোথাও চরাইতে লইয়া গিয়াছে। মেয়েরা আপন আপন গৃহকর্মে ব্যস্ত, তাহারা কেহই মুচকুন্দের উত্তর দিল না। দুই-একজন মাটি কোপাইয়া মাটির বড় বড় চাঙর তুলিতেছে, পরে জল দিয়া ভিজাইয়া ঘরের দেওয়াল দেওয়া হইবে। মাত্র একজন আধবয়সী সাঁওতাল এক জায়গায় বসিয়া একটি কাঠের পুতুল লইয়া কি করিতেছিল। পুতুলটার কোমর হইতে বেশ এক ফালি কাপড় ঘাঘরার মত পরানো। এই ঘাঘরার মধ্যে হাত পুরিয়া ভিতরে সে পুতুলটাকে ধরিয়া আছে। হাঁক-ডাক করিতে করিতে মুচকুন্দ সেখানে আসিয়া তাহাকে বলিল, আরে চল্ উধার, বাবু আসিয়াছে তুদের পাড়া দেখতে।
মাঝি নিবিষ্টমনে আপন কাজ করিতে করিতে বলিল, সি-তু বলগা যেয়ে মোড়ল মাঝিকে। আমি এখন যেতে লাড়ব।
কৌতূহলপরবশ হইয়া মুচকুন্দ প্রশ্ন করিল, উঠা কি আসে রে? কেয়া করেগা উ লেকে?
মাঝি হাতটা বাড়িয়ে পুতুলটা মুচকুন্দের মুখের কাছেই ধরিল, পুতুলটা সঙ্গে সঙ্গে দুইটি হাতে তালি দিয়া মাথা নাড়িতে আরাম্ভ করিল। মুচকুন্দ আপনার মুখ খানিকটা সরাইয়া লইয়া মুগ্ধভাবেই বলি, আ-হা।
কয়টি তরুণী মেয়ে আঙিনা পরিস্কার করিতেছিল, তাহারা খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। ইহার মধ্যে কখন একটা ছেলে ছুটিয়া চলিয়া গিয়াছিল মোড়ল মাঝির নিকট, সংবাদ পাইয়া কমল মাঝি ঠিক এই সময়েই আসিয়া উপস্থিত হইল। মুচকুন্দের সম্মুখে দাঁড়াইয়া সে বেশ বিনয়সহকারেই বলিল, কার সিপাই বটিস গো তু? বুলছিস কি?
মুচকুন্দ বলিল, ইন্দর রায়, ছোট তরফ। চল, বাহারমে হুজুর দাঁড়াইয়ে আসেন।
মাঝি ব্যস্ত হইয়া আদেশ করিল, চৌপায়া নিয়ে আয়।
রায় এতক্ষণ চারিদিক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। পূর্বপশ্চিমে লম্বা চরটা পাঁচ শ বিঘা হইবে না, তবে তিন শ বিঘা খুব। হাতে খানিকটা মাটি তুলিয়া লইয়া তাহাও পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন।
মাটির ঢেলাটা আয়তনের অনুপাতে লঘু। সূক্ষ্ম বালুকাগুলি সূর্যকিরণে ঝিকমিক করিতেছে। বুঝিলেন, উর্বরতায় যাকে বলে স্বর্ণপ্রসবিনী ভূমি-এ তাই। আবার একবার চারিদিকে দৃষ্টি বুলাইয়া তিনি চরটার সংলগ্ন এ-পারে গ্রামখানার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন। এ গ্রামখানা চক-আফজলপুর, চক্রবর্তীদের সম্পত্তি। এটার সম্মুখীন হইলে তো চরটা হইবে চক্রবর্তীদের। কিন্তু ঠিক কি চক-আফজলপুরের সম্মুখেই পড়িতেছে? আকাশের দিকে চাহিয়া তিনি তরুণ সূর্য এবং আপনার ছায়াকে এক রেখায় রাখিয়া দাঁড়াইলেন। তাহা হইলে চক-আফজলঅউর একবারে উত্তরে। অন্তত বারো আনা চর আফজলপুরের সীমানাতেই পড়িবে। একেবারে পশ্চিম প্রান্তের এক চতুর্থাংশ-চার আনা রায়বংশের সীমানায় পড়িতে পারে। রায় হাসিলেন, মাটি বাপের নয়, মাটি দাপের। ইহারও প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু রাধারাণির সন্তানের ভোগ্যবস্তু তাহার সপত্নীপুত্র ভোগ করিবে এইটাই তাহার কাছে মর্মান্তিক।
মাঝি আসিয়া ঈষৎ নত হইয়া রায়কে প্রণাম করিল; একটা ছেলে চৌপায়াটা আনিয়া দিল। রায় হাতের ছড়িটাকে চৌপায়ার উপর রাখিয়া ছড়িটার উপর ঈষৎ ভর দিয়া দাঁড়াইলেন, বসিলেন না। তার পর প্রশ্ন করিলেন, তুই এখানকার মোড়ল মাঝি?
হাতজোড় করিয়া মাঝি উত্তর দিল, হ্যাঁ বাবুমশায়।
হুঁ। কতদিন এসেছিস এখানে?
তা আজ্ঞা, এক দুই তিন মাস হবে গো; সেই কার্তিক মাসে এসেই তো এখানে আলু লাগালাম গো।
হাসিয়া রায় বলিলেন, বুঝলাম, ছ মাস হ’ল এসেছিস। কিন্তু কাকে বলে বসলি এখানে তোরা?
কাকে বুলব? দেখলাম জঙ্গল জমি, পড়ে রয়েছে, বসে গেলাম।
সুগভীর গাম্ভীর্যের সহিত তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রায় বলিলেন-এ চর আমার।
মাঝি বলিল, সি আমরা জানি না।
আমাকে কবুলতি দিতে হবে, এখানে বাস করতে হলে কবুলতি লিখে দিতে হবে।
মাঝি সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে রায়ের দিকে চাহিয়া বলিল, সেটো আবার কি বেটে গো?
কাগজে লিখে দিতে হবে যে, আপনি আমাদের জমিদার, আপনাকে আমরা এই চরের খাজনা কিস্তি কিস্তি দিয়ে মিটিয়ে দেব। তারপর সেই কাগজে তোরা আঙ্গুলের টিপছাপ দিবি।
মাঝি চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল, যেন কথাটা হৃদয়ঙ্গম করিবার চেষ্টা করিতেছে। রায় বলিলেন, কথাটা বুঝলি তো? কবুলতি লিখে দিতে হবে।
ইহারই মধ্যে সাঁওতালদের মেয়েগুলি আসিয়া এক পাশে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া খুব গম্ভীরভাবে সমস্ত কথা শুনিতেছিল, মৃদুস্বরে আপনাদের ভাষায় পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করিতেছিল। মাঝির নাতনীটি এবার বলিয়া উঠিল, কেনে, তা লিখে দিবে কেনে? টিপছাপটি লিখে দিবে কেনে?
নইলে এখানে থাকতে পাবি না।
মেয়েটিই বলিল, কেনে, পাব না কেনে?
না, চর আমার। থাকলে হলে কবুলতি দিতে হবে।
এতক্ষণে মাঝি ঘাড় নাড়িয়া প্রস্তাবে অস্বীকৃতি জানাইয়া বলিল, উঁহু।
ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া রায় বলিলেন, ‘উঁহু’ বললে তো চলবে না মাঝি। প্রজা বন্দোবস্তির এই নিয়ম, কবুলতি না দিলে চলবে না।
সেই মেয়েটি বলিয়া উঠিল, তুরা যদি খত লিখে লিস, এক শ, দু শ টাকা পাবি লিখিস?
রায় হাসিয়া ফেলিলেন, না না, সে ভয় নেই, তা লিখে নেব না। জমিদার কি তাই কখনও করে?
মেয়েটি বলিল, করে না কেনে? ঐ-উ গাঁয়ে, সি গাঁয়ে লিখে লিলি যি!
মাঝি এবার বলিল, তবে সিটো আমরা শুধাবো আমাদের রাঙাবাবুকে, সি যদি বলে তো, দিবো টিপছাপ।
রায়ের মুখ রক্তোচ্ছাসে লাল হইয়া উঠিল, তিনি গম্ভীরভাবে শুধু বলিলেন, হুঁ। তারপর পল্লীর দিকে পিছন ফিরিয়া ডাকিলেন, মুচকুন্দ সিং!
মুচকুন্দ তখন সেই পুতুল নাচের ওস্তাদ সাঁওতালটির সহিত জমাইয়া বসিয়াছিল। সে চুন ও তামাকের পাতা সংযোগে খৈনি প্রস্তুত করিতেছিল; আর ওস্তাদ নানা ভঙ্গিতে নাচিতে নাচিতে বোল বলিতেছিল- চিলক, চিলক, চিলক। সঙ্গে সঙ্গে তাহার কাঠের পুতুলটাও ঘাড় ও মাথা নাড়িয়া তালে তালে তালি দিতেছিল, খটাস, খটাস, খটাস।
মুচকুন্দ বিস্ময়বিমুগ্ধ হইয়া বসিয়া বসিয়া তারিফ করিতেছিল। প্রভুর ডাক শুনিয়া সে বলিল, গাঁওমে যাস্ মাঝি, রোজকার হবে তোর।
.
রায়-বংশ শাখাপ্রশাখায় বহুধাবিভক্ত। আয়ের দিক দিয়া বাৎসরিক পাঁচ শত টাকার আয় বড় কাহারও নাই। কেবল ছোট বাড়ি আজ তিন পুরুষ ধরিয়া এক সন্তানের বিশেষত্বের কল্যাণে এখনও উহারই মধ্যে সমৃদ্ধিসম্পন্ন। ইন্দ্রচন্দ্র রায়ের বাৎসরিক আয় দেড় হাজার হইতে দুই হাজার হইবে। আর ও-দিকে মাঝের বাড়ি অর্থাৎ রামেশ্বর চক্রবর্তী রায়েদের সম্পত্তির তিন আনা চার গণ্ডা বা এক-পঞ্চমাংশের অধিকারী। তাহার অংশের আয় ওই হাজার দুইয়েক টাকা আয় অল্প হইলেও ইন্দ্র রায়ের প্রতাপ এ অঞ্চলে যথেষ্ট। রামেশ্বর চক্রবর্তীর মস্তিষ্ক বিকৃতির পর ইন্দ্র রায়ের এখন অপ্রতিহত প্রতাপ। বাড়ি ফিরিয়া তিনি সাঁওতাল পল্লীতে দশজন লাঠিয়াল পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন; আদেশ দিলেন, ঠিক বেলা তিনটার সময় মাঝিদের ধরিয়া আনিয়া কাছারিতে বসাইয়া রাখিবে। সেইটাই তাহাদের খাইবার সময়। সাধারণতঃ সাঁওতালেরা অত্যন্ত নিরীহ প্রকৃতির জাতি–মাটির মত; উত্তপ্ত সহজে হয় না, কখনও কখনও ভিতর হইতে প্রলয়গ্নিশিখা বুক ফুটিয়া বাহির হইয়া পড়ে বটে, কিন্তু সেও শতাব্দীতে একবার হয় কি না সন্দেহ।
অপরাহ্নের দিকে লাঠিয়ালরা গিয়া তাহাদের আনিয়া ছোট বাড়ির কাছারিতে আটক করিল। ইন্দ্র রায় বাড়িতে তখনও দিবানিদ্রায় মগ্ন। মোড়ল মাঝি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিল, কই গো, বাবুমশায় কই গো? একসঙ্গে সাত-আটজন লাঠিয়াল সমস্বরে গর্জন করিয়া উঠিল, চো-প!
কাছারি বাড়ির সাজসজ্জা আজ একটু বিশিষ্ঠ রকমের, সাধারণ অবস্থার চেয়ে জাঁকজমক অনেক বেশি। কাছারি-ঘরে প্রবেশের দরজার দুই পাশে বারান্দায় দেওয়ালের গায়ে গুণচিহ্নের ভঙ্গীতে আড়াআড়িভাবে দুইখানা করিয়া চারিখানা তলোয়ার ঝুলিতেছে, দুইদিকেই মাথার উপরে এক একখানা ঢাল। ইন্দ্র রায়ের বসিবার আসন ছোট তক্তপোশটার উপর একটা বাঘের চামড়া বিছানো। মুচকুন্দ সিং প্রকাণ্ড পাগড়ি বাঁধিয়া উর্দি ও তকমা আঁটিয়া ছোট একটা টুলের উপর বসিয়া আছে। সাঁওতালেরা অবাক হইয়া সমস্ত দেখিতেছিল। ইন্দ্র রায় কূটকৌশলী ব্যক্তি, তিনি জানেন চোখে ধাঁধা লাগাইতে না পারিলে সম্ভ্রমের জাদুতে মানুষকে অভিভূত করিতে পারা যায় না। চাপরাসী নায়েব সকলেই ফিসফাস করিয়া কথা কহিতেছিল, এতটুকু জোরে শব্দ হইলেই নায়েব ভ্রুকুটি করিয়া বলিতেছিল, উঃ!
অচিন্ত্যবাবু প্রত্যহ অপরাহ্নে এই সময়ে ইন্দ্র রায়ের নিকট আসেন। তিনি আসিয়া সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া একটু শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। নায়েবের নিকট আসিয়া চুপিচুপি প্রশ্ন করিলেন, ব্যাপার কি মিত্তির মশায়? এত লোকজন, ঢাল-তরোয়াল? কোন দাঙ্গা টাঙ্গা নাকি?
মিত্তির হাসিয়া মৃদুস্বরে উত্তর দিলেন,-বাবুর হঠাৎ খেয়াল আর কি!
অচিন্ত্যবাবুর দৃষ্টি ততক্ষণে কমল মাঝির উপর পড়িয়াছিল, তিনি শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন, সর্বনাশ! সাক্ষাৎ যমদূত! আচ্ছা, আমি চললাম এখন, অন্য সময় আসব।
বসবেন না?
উঁহু। একটু ব্যস্ত আছি এখন। মানে ওই চরটায় শুনেছি অনেক রকমের ওষুধের গাছ আছে। তাই ভাবছি, কলকাতায় গাছগাছড়া চালানের একটা ব্যবসা করব। তারই প্ল্যান-হিসেব নিকেশ করতে হবে। তিনি চলিয়া গেলেন।
প্রায় ঘন্টাখানেক পরে ইন্দ্র রায় কাছারিতে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। সকলে সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল। দেখাদেখি সাঁওতালরাও উঠিয়া দাঁড়াইল। ইন্দ্র রায় আসন গ্রহণ করিয়া কর্মান্তরে মনোনিবেশ করিলেন, অজ্ঞাত অভুক্ত সাঁওতাল দল নীরবে জোড়হাত করিয়া বসিয়া রহিল। কাছারি-বাড়ির দরজায় কয়টি সাঁওতালের মেয়ে কখন আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহারা আশঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া আপন আপন বাপ-ভাই-স্বামীর সন্ধানে আসিয়াছে। আপনাদের ভাষায় তাহারা কথা বলিতে বলিতে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া আসিল।
ইন্দ্র রায় লাঠিয়ালদিগকে কি ইঙ্গিত করিলেন, একজন লাঠিয়াল অগ্রসর হইয়া গিয়া মেয়েদের বাধা দিয়া বলিল, কি দরকার তোদের এখানে? যা, এখানে গোলমাল করিস নি।
কমলের নাতনী-দীর্ঘাঙ্গী মেয়েটি বলিল, কেনে তোরা আমাদের লোককে ধরে এনেছিস?
বৃদ্ধ কমল মাঝি আপন ভাষায় তাহাদের বলিল, যাও যাও, তোমরা বাড়ি যাও। বাবু রাগ করবেন। সে বড় খারাপ হবে।
মেয়েগুলি সভয়ে ক্ষুণ্ণ মনেই চলিয়া গেল।
এতক্ষণে বৃদ্ধ মাঝি করজোড়ে বলিল, আমরাও এখুনও খাই নাই বাবু, ছেড়ে দে আমাদিগে। ইন্দ্র রায় বলিলেন, কবুলতিতে টিপছাপ দিয়ে বাড়ি চলে যা।
মাঝি বলিল, হাঁ বাবু, সিটি কি করে দিবো? আমাদের রাঙাবাবুকে আমরা গিয়ে শুধোই, তবে তো দিবো।
নায়েব ধমক দিয়া উঠিলেন, রাঙাবাবু কে রে? তাকে কি জিজ্ঞেস করবি? টিপছাপ দিতে হবে।
অদ্ভুত জাত, বিদ্রোহও করে না, আবার ভয়ও করে না, কমল মাঝি ঘাড় নাড়িয়া বলিল, উঁহু।
আবার সাঁওতালদের মেয়েগুলির কলরব ফটক-দুয়ারের সম্মুখে ধ্বনিত হইয়া উঠিল। আবার উহারা ফিরিয়া আসিয়াছে। রায়ের মনে এবার করুণার উদ্রেক হইল, আহা! কোনোমতেই ইহাদের এখানে রাখিয়া যাইতে বেচারাদের মন উঠিতেছিল না। যাইতে যাইতে আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। তিনি একজন লাঠিয়ালকে বলিলেন, দরজা খুলে ওদের আসতে বল। তিনি স্থির করিলেন, সকলেই এখানে আহার করাইয়া আজিকার মত অব্যাহতি দিবেন টিপসই উহারা স্বেচ্ছায় দিয়া যাইবে।
লাঠিয়াল অগ্রসর হইবার পূর্বেই কিন্তু ফটকের দরজা খুলিয়া বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিল অহীন্দ্র। তাহার পিছনে পিছনে ওই মেয়েগুলি। রায় বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। সুকঠিন ক্রোধে বজ্রের মত তিনি উত্তপ্ত এবং উদ্যত হইয়া উঠিলেন।
অহীন্দ্র আসিয়া প্রণাম করিয়া হাসিমুখে বলিল, এদের ছেলেমেয়েরা কাঁদছে মামাবাবু। ভয়ে আপনার সামনে আসতে পারছে না। এ বেচারারা এখনও স্নান করে নি, খায় নি, এখন কি এমনি করে বসিয়ে রাখতে আছে? এদের ছেড়ে দিন।
অহীন্দ্র এতগুলি কথা বলিয়া গেল, বজ্রগর্ভ অন্তরেই রায় বসিয়া রহিলেন, কিন্তু ফাটিয়া পড়িবার তাঁহার অবসর হইল না। মুহূর্তে মুহূর্তে অন্তর্লোকেই সে বিদ্যুৎশিখা এ-প্রান্ত হইতে ও-প্রান্ত পর্যন্ত দগ্ধ করিয়া দিয়া তাঁহাকে বর্ষণোন্মুখ করিয়া তুলিল। সহসা তাঁহার মনে হইল, রাধারাণীর ছেলেই যেন তাঁহাকে ডাকিতেছে, মামাবাবু!
অহীন্দ্র এবার সাঁওতালদের বলিল, যা, তোরা বাড়ি যা এখন, আবার ডাকতে গেলেই আসবি, বুঝলি?
সাঁওতালেরা হাসিমুখে উঠিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু একজন লাঠিয়াল বলিয়া উঠিল, খবরদার বলছি, ব’স সব, বস।
এতক্ষণে বজ্রপাত হইয়া গেল, দারুণ ক্রোধে ইন্দ্র রায় গর্জন করিয়া উঠিলেন, চোপরাও হারামজাদা! তারপর সাঁওতালদের বলিলেন, যা, তোরা বাড়ি যা।