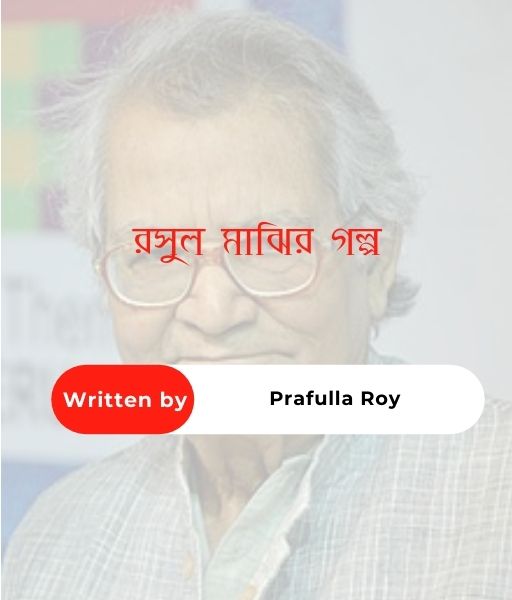আরণ্যক (Aronyak)
ভাই টুপুদি,
মাসখানেক হল কানপুর থেকে আমরা ফরাসগাঁও এসেছি। জায়গাটা মধ্যপ্রদেশের সুদূর অভ্যন্তরে। এখানে দাঁড়িয়ে যে দিগন্তেই চোখ ফেরাই, শুধু পাহাড় আর পাহাড়। নীলাভ পাহাড়গুলো ঘর অরণ্যে রোমঞ্চিত হয়ে আছে। একটু ব্যাখ্যা করে বলি। রামায়ণে দণ্ডকারণ্যের কথা পড়েছিস তো। এ হল সেই জায়গা। সে-যুগে রামচন্দ্র এখনে বনবাসে এসেছিলেন। এ-যুগে পূর্ব বাংলার উদ্বাস্তুদের জন্য অরণ্য সংহার করে উপনিবেশ গড়ে উঠছে। খবরের কাগজের কল্যাণে এ খবর নিশ্চয়ই তোর অজানা নয়। সমস্ত এলাকাটা জুড়ে বিচিত্র এক জীবনযজ্ঞ শুরু হয়ে গেছে যেন।
সে যাই হোক, আমাদের ফরাসগাঁও আসার কারণটা এবার বলি। তোর ভগ্নীপতিটিকে তো জানিস একটা আস্ত বেদে। দুটো দিন কোথাও যদি স্থির হয়ে থাকতে পারে! ছবছর বিয়ে হয়েছে। এর মধ্যে কত চাকরি যে ছাড়ল, কত চাকরি ধরল আর নতুন নতুন কত জায়গায় না ঘুরল! এই ভ্ৰমণবাগীশটিকে নিয়ে আর পারি না।
তুই তো জানিস, বিয়ের পরই আমরা বোম্বাই চলে গিয়েছিলাম। ও তখন সেখানে চাকরি করত। বোম্বাই থেকে দুমাস পরেই গেলাম ভাইজাগ, ভাইজাগ থেকে পাঞ্জাব, পাঞ্জাব থেকে মাদ্রাজ সারা ভূমণ্ডল পাড়ি দিয়ে শেষ পর্যন্ত কানপুরে এসে বছরখানেক ছিলাম। ভেবেছিলাম, এতদিনে বেদেটা বুঝি শান্ত হল। কিন্তু ও মা, বলা নেই কওয়া নেই, হঠাৎ কানপুরের চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে দণ্ডকারণ্য প্রোজেক্টে কাজ জুটিয়ে ফেলল। অগত্যা ফরাসগাঁও না এসে উপায় কী!
জানিস ভাই, এখানে একেবারে আরব্য রজনীর ব্যাপার। এখনও বাড়িঘর তৈরি হয়নি। তাঁবুর ভেতর থাকার ব্যবস্থা। তোর ভগ্নীপতিটির পাল্লায় পড়ে বাংলাদেশের ভীরু মেয়ে আমি, পুরোদস্তুর আরব বেদুইন বনে গেছি।
যাই হোক, প্রথম প্রথম ভীষণ ভয় করত। তাঁবু ছেড়ে এক পা-ও বেরুতাম না। ইদানীং ভয়টা গেছে। ধীরে ধীরে, সত্যি বলছি ভাই, দণ্ডক-বনের প্রেমে পড়ে গেছি। আমাদের এই ফরাসগাঁও থেকে দক্ষিণে গেলে চিত্রকুট। সেখানে চমৎকার একটা ফল্স্ আছে। কিন্তু এই বাহ্য। এখান থেকে উত্তরে পাড়ি জমালে কেশকাল পাহাড়ের চুড়ো সেখানে কাঁচ দিয়ে ঘেরা একটা রেস্ট হাউস আছে। চার পাশে নিবিড় বন–মধ্যপ্রদেশের রিজার্ভ ফরেস্ট। যে কোনও একটা রাত্রি সেখানে গিয়ে থাকলে কাচের স্বচ্ছ দেওয়ালের ওপরে দেখা যাবে বাঘ ভালুক আর বাইসনেরা ইচ্ছামতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। দেখতে দেখতে রোমাঞ্চ হয়। ভয়ও লাগে। মনে হ্য, সভ্যতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বহু শতাব্দী আগের এক হিংস্র আদিম জগতে ফিরে গেছি। ইতিমধ্যেই দুরাত আমরা সেখানে কাটিয়ে এসেছি। কেশকাল পাহাড়ের চুড়া আমার মনোহরণ করেছে।
ভাই টুপুদি, মনে পড়ে বিয়ের আগে মাঝে মাঝেই আমরা চিড়িয়াখানায় যেতাম। পিঞ্জরাবদ্ধ পশুগুলোকে দেখে তোর খারাপ লাগত। বলতিস ওদের মুক্ত প্রকৃতির মাঝখানে দেখতে ইচ্ছে করে। সংসার থেকে দিনকয়েকের ছুটি নিয়ে চলে আয় না। কেশকাল পাহাড়ের চুড়োয়, প্রকৃতির সেই স্বদেশে তোর ইচ্ছেপূরণ করে নিতে পারবি।
আমি জানি তোর ভগ্নীপতিটি এবং আমার ভগ্নীপতিটি–দুই ভায়রা একেবারে উল্টো স্বভাবের মানুষ। তোরটি বনের পাখি, সব সময় খালি উড়ু উড়ু। আমারটি খাঁচার পাখি। তা ভাই কয়েকটা দিনের জন্য খাঁচার পাখিটাকে দণ্ডকবনের অবাধ আকাশে এনে ছেড়ে দে।
দুবছর তোরও বিয়ে হয়েছে। এর মধ্যে কলকাতার ভিতর থেকে একটা দিনের জন্যেও বেরুসনি। অথচ ছেলেবেলা থেকেই বেড়াবার কত সাধ তোর। বিয়ের আগে এ নিয়ে কত গল্পই না করতিস। বোম্বাইতে থাকতে, পাঞ্জাবে থাকতে, কি কানপুরে থাকতে কতবার তোকে যেতে লিখেছি। তুই যাসনি। এবার কিন্তু কোনও অজুহাতই শুনব না। জামাইবাবু একান্ত না এলে ছেলেপুলেদের রেখে একাই চলে আসবি, নিশ্চই আসবি। কোনও অসুবিধে নেই। বোম্বাই মেলে রায়পুর স্টেশন থেকে আমরা তোকে নিয়ে আসতে পারব। যদি না আসিস জন্মের মতো আড়ি। ইতি–মঞ্জু।
বিকেলের ডাকে চিঠিটা এসেছে। একবার, দুবার, তিনবার, কতবার যে চিঠিখানা পড়ল শোভনা! তার আদরের নাম টুপু।
মঞ্জু তার আপন বোন নয়, ছোট কাকার মেয়ে। জেঠতুতো খুড়তুতো বোনদের মধ্যে মঞ্জুর জন্যেই শোভনার আকর্ষণটা সবচেয়ে বেশি। প্রায় আশৈশব। তার জন্যে মঞ্জুরও প্রাণের টান প্রবল। বোন বলল যথেষ্ট বলা হয় না; মঞ্জু ছিল তার সখী। বিয়ের আগে চলাফেরা ওঠা-বসা–সবই ছিল একসঙ্গে। স্কুল-কলেজে একই ক্লাসে পড়ত। তাছাড়া দুজনে প্রায় সমবয়সিও। শোভনা খুব বেশি হলে বছরখানেকের বড়।
কাকারা জেঠারা এবং শোভনারা নদীয়া জেলার এক মফস্বল শহরে একই বাড়িতে থাকত। একই বাড়িতে, তবে এক অন্নে আবদ্ধ ছিল না। বাড়িটা ছিল পূর্ব পুরুষের। শোভনার বাবা-কাকারা সেটা ভাগাভাগি করে নিয়েছিলেন। কাজেই বিয়ের আগে পর্যন্ত শোভনা আর মঞ্জু ছিল সর্বক্ষণ পরস্পরের সহচরী, সঙ্গিনী।
যাই হোক, বি.এ পড়তে পড়তেই দুজনের বিয়ে হয়ে গিয়েছিল এবং তা-ও মাসখানেকের মধ্যেই। প্রথমে মঞ্জুর, পরে শোভনার। বিয়ের পর বোম্বাই চলে গিয়েছিল মঞ্জু। আর শোভনা এসেছিল কলকাতায়।
কলকাতা বললে ঠিক বোঝানো যায় না। এই শহরের পূর্ব মেরুতে এক জন্মান্ধ রুদ্ধশ্বাস গলির শেষ প্রান্তে জীর্ণ ধ্বংসপ্রায় একটা বাড়িতে তাকে এনে তুলেছিল শশাঙ্ক। সেখানে এজমালি একখানা উঠোন ঘিরে বৃত্তাকারে সারিবদ্ধ ঘর। সেই ঘরগুলির একটিতে শশাঙ্কর সংসার।
কলকাতার এই অংশের এই বাড়িটিতে শীত-গ্রীষ্ম কোনও ঋতুই স্পষ্ট করে বোঝা যায় না। সবসময় যেন ছায়া-ছায়া বিষণ্ণ বিকেল। সূর্য বিষুবরেখায় না গেলে এ বাড়িতে রোদ আসে না।
শোভনার বিয়ে হয়েছে ছবছর। ছবছর, অর্থাৎ একটা যুগের অর্ধেক। এর ভেতর বার দুই নদীয়ায় যাওয়া ছাড়া সময়ের এই বিরাট অংশটা আলো-বাতাস-বর্জিত রুদ্ধ গলিতেই কেটে গেল। এর মধ্যে সংসার বেড়েছে। দুটি ছেলে আর একটি মেয়ে হয়েছে।
চিঠিটা হাতের মুঠোতেই ছিল। হঠাৎ সমস্ত স্নায়ুতে কেমন এক অস্থিরতা অনুভব করল শোভনা। ছটা বছর পূর্ব কলকাতার এই বিবরে আবদ্ধ হয়ে আছে সে। অথচ-অথচ বিয়ের আগে আশ্চর্য যাযাবর একখানা মন ছিল তার। হিল্লি-দিল্লি, কাশী-কাঞ্চী—ভারতবর্ষের দুর দিগন্তগুলি দুর্বার আকর্ষণে তাকে টানতে থাকত। বিশেষ করে অরণ্যের প্রতি তার মোহ ছিল তীব্র। কিন্তু বেড়াতে নিয়ে যাবার মতো সঙ্গতি তার বাবার ছিল না। কাজেই মনসা-মথুরাং আর ভ্রমণকাহিনি পড়েই শব্দ মেটাতে হত। মনে মনে নিরুচ্চার একটা স্বপ্ন ছিল, তেমন কারো হাতে গিয়ে যদি পড়ে, বিয়ের পর সব সাধ মিটিয়ে নেবে। তেমন বিয়ে তো প্রায় স্থিরই হয়ে গিয়েছিল। সেটা হলে আজ মঞ্জুর বদলে সে-ই তো–কিন্তু–চিঠিটা হাতে নিয়ে আত্মবিস্মৃতের মতো কতক্ষণ বসে ছিল খেয়াল নেই। হঠাৎ ছোট ছেলেটা তক্তপোষের ওপর ঘুম ভেঙে কেঁদে উঠল। ঘোর কেটে গেল শোভনার। ইতিমধ্যে বিকেলটা কখন যেন নিঃশেষ হয়ে গেছে। পূর্ব কলকাতার জন্মান্ধ গলির পটে সন্ধে নামতে শুরু করেছে।
সন্ধের পর শশাঙ্ক অফিস থেকে ফিরে এল। চা-খাবার খাওয়া হলে বিকেলের সেই চিঠিখানা তার হাতে দিল শোভনা।
শশাঙ্কর মুখটা চতুষ্কোণ, চোখ দুটি পিঙ্গল। দৃষ্টিতে কোনও ভাবের খেলাই খেলে না। তার দিকে তাকালে স্নায়ুতে ধাক্কা লাগে যেন। মনে হয় এই লোকটির অদৃশ্য গভীরে কোথায় যেন খানিকটা নিষ্ঠুরতা রয়েছে। যাই হোক নিরুৎসুক সুরে শশাঙ্ক বলল, কী ব্যাপার, কার চিঠি?
শোভনা বলল, পড়েই দেখো না।
পড়তে পড়তে শশাঙ্কের পিঙ্গল চোখে কীসের একটা ছায়া পড়ল যেন। কিন্তু তা মুহূর্তের জন্যই। দ্রুত পড়া শেষ করে এক সময় নিস্পৃহ ভাববর্জিত মুখে চিঠিটা শোভনার হাতে ফিরিয়ে দিল সে।
সাগ্রহে শোভনা বলল, পড়লে?
হুঁ। শশাঙ্কের গলা থেকে সংক্ষিপ্ত একটা শব্দ বেরিয়ে এল।
তা হলে মঞ্জুকে কী লিখব?
এত তাড়াহুড়োর কী আছে। বলতে বলতে শশাঙ্ক উঠল, যাই, আজকের বাজারটা সেরে রাখি। কাল একটু তাড়াতাড়ি বেরুতে হবে। সকালে সময় পাব না।
দণ্ডকারণ্য তার সমস্ত অস্তিত্বের মধ্যে তরঙ্গ তুলেছে। কাল শশাঙ্ক বলেছিল ব্যস্ততার কিছু নেই। কিন্তু পরের দিনই আবার সেই প্রশ্নটা তুলল শোভনা, কটা দিন ছুটি নিয়ে চলো না, মঞ্জুদের ওখানে বেড়িয়ে আসি?
ইয়ার এন্ডিং হয়ে আসছে। দুমাসের মধ্যে এখন অফিস থেকে ছুটি পাওয়া যাবে না।
বেশ তো, ইয়ার এন্ডিং-এর পরই না হয় যাওয়া যাবে?
দেখি।
দুটো মাস আশায় আশায় রইল শোভনা। ইতিমধ্যে আরো তিনখানা চিঠি এসেছে মঞ্জুর। এদিকে ইয়ার এন্ডিং-এর ঝামেলা চুকে গেছে শশাঙ্কের। অতএব নিষ্কণ্টক। শোভনা বলল, এবার ছুরি নাও।
প্রথমটা নিরুত্তর রইল শশাঙ্ক।
শোভনা বলতে লাগল, ছবছর ধরে ওরা চিঠি লিখছে-বোম্বাই-পাঞ্জাব ভাইজাগ–যেখানেই গেছে আমাদের যাবার জন্যে কত করে বলছে। কিন্তু কোথাও আমাদের যাওয়া হয়নি। ভেবে দেখো এবার না গেলে খুব খারাপ দেখাবে।
এবার মুখ খুলল শশাঙ্ক যাবে যাবে তোতা বলছ। কিন্তু খরচটার কথা ভেবেছ। হিসেব করে দেখ যাতায়াতের গাড়িভাড়া কত পড়ে। তাছাড়া ওখানে গেলে হাত টেনে চলা যাবে না। রীতিমতো খরচ করতে হবে। এবার যাওয়া বরং স্থগিত রাখো। পরে সুবিধামতো এক সময়
ছ বছর ধরে এই রকম এক-একটা অজুহাত খাড়া করে তার যাওয়া বন্ধ রেখেছে। শশাঙ্ক। প্রতিবারই শান্ত সহিষ্ণু মুখে সব মেনে নিয়েছে শোভনা। কিন্তু এবার যেন কী হয়ে গেল তার। ক্ষিপ্তের মতো বলে উঠল, কোথাও একটু বেরুতে পারি না। দম আমার বন্ধ হয়ে আসছে। ছবছর এ নরকে আমাকে আটকে রেখেছ। কিন্তু
কথা শেষ হল না তার। শশাঙ্কের ভাববর্জিত পিঙ্গল চোখ দুটা দপ করে উঠল। শোভনার মুখের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে সে দাঁতে দাঁত চাপল, নরক! আমি কিছুই লুকোইনি। তোমার বাবা এই নরক দেখেও তোমাকে আমার হাতে দিয়েছে। তাকে বললেই পারত একটা স্বর্গ ফুটিয়ে দিত।
শোভনা মরিয়ার মতো বলতে লাগল, তোমার কোনও কথা শুনতে চাই না। তুমি না যাও আমাকে রেহাই দাও। এখানে আমি আর পারছি না। এবার আমি মঞ্জুদের কাছে যাবই।
তা তো যাবেই। নইলে অনিমেষের সঙ্গে রাসলীলা চালাবে কেমন করে! ব্যঙ্গে ঠোঁট দুটো বেঁকে গেল শশাঙ্কের।
কী, কী বললে!
যা বলেছি তা তো শুনেছই।
মুখ সামলে কথা বলবে।
একমুহূর্ত থমকে রইল শশাঙ্ক। পরক্ষণেই গর্জে উঠল, কেন তোর ভয়ে! সত্যি কথাটা বলতেই গায়ে বুঝি ফোঁসকা পড়ল। মনে করেছিস আমি কিছুই জানি না। তোর সঙ্গেই তো বিয়ে হবার কথা ছিল অনিমেষের। বিয়ের আগে।
শুনতে শুনতে শশাভনার মনে হল, একেবারে অন্ধ আর বধির হয়ে গেছে। ব্যাপারটা নিতান্তই তুচ্ছ। মঞ্জুর স্বামী অনিমেষ ছিল নদীয়া জেলায় তাদের সেই মফস্বল শহরেরই ছেলে। শোভনাদের বাড়িতে খুবই যাতায়াত ছিল। প্রচুর হাসতে পারত সে। মজা করতে, গল্প জমাতে বিশারদ ছিল। গানের গলাখানি চমৎকার। ভালো ফুটবল খেলতে পারত। তার ওপর ছিল প্রিয়দর্শন, সুপুরুষ। মফস্বল শহরের ছোট্ট পরিধির মধ্যে থাকত, বাড়িতে যাওয়া-আসা ছিল। স্বাভাবিক নিয়মেই শোভনার সঙ্গে আলাপ হয়েছে। মনেও রঙ লেগেছে। সেই রঙ গাঢ় হয়েছিল যখন তার সঙ্গে বিয়ের কথা উঠল। কথাটা অনেকদূর এগিয়েছিল। কিন্তু পাকাপাকি হবার পর্যায়ে এসে ভেঙে যায়। কেননা অনিমেষের বাবার দাবি পূরণ করা শোভনার বাবার পক্ষে অসাধ্য ছিল। এদিকে ছোটকাকা এমন একটি শিকার হাতছাড়া করলেন না। কন্ট্রাক্টরির দৌলতে তার প্রচুর টাকা। অতএব অনিমেষের সঙ্গে মঞ্জুর বিয়ে হয়ে গেল। আর শোভনার বাবা হন্যের মতো খুঁজে খুঁজে শশাঙ্ক নামে মার্চেন্ট অফিসের এক কেরানিকে আবিষ্কার করলেন। যাই হোক, বিয়ের পর চেতনে বা অবচেতনে প্রাক-বিবাহ সেই রঙের চিহ্নমাত্র ছিল না। নিজের দীন সংসার, ছেলেমেয়ে এবং শশাঙ্ককে নিয়েই পরিতৃপ্ত হতে চেয়েছিল শোভনা।
এদিকে শশাঙ্ক থামেনি। সামনে গজরাচ্ছে। কেন যে মঞ্জুদের ওখানে যাবার জন্য তোর প্রাণ আঁকুপাঁকু–সব জানি। কিন্তু তা হবে না। ছবছর যেতে দিইনি। কোনওদিন দেবও না। ভেবেছিস
শশাঙ্কর পিঙ্গল চোখ দুটি জ্বলছে। গলার কাছে শিরাগুলো দড়ির মতো পাকিয়ে পাকিয়ে উঠেছে। সন্দিগ্ধ চতুষ্কোণ মুখটা কী নিষ্ঠুরই না হয়ে উঠেছে। সব মিলিয়ে শশাঙ্ক যেন মানুষ না, একটা আদিম হিংস্র পশু।
শোভনার মনে হল, কোথাও যেতে হয় না। বিশ শতকের এই সভ্য সুসজ্জিত কলকাতাও মাঝে মাঝে অরণ্য হয়ে উঠতে পারে। সেই রাত্রেই মঞ্জুকে চিঠি লিখল শোভনা, মঞ্জু, বাঘ-ভালুক দেখার জন্যে আমাকে যেতে লিখেছিস। নতুন করে অতদূরে কী আর দেখতে যাব বল। দণ্ডকারণ্যের জন্য এতটুকু আকর্ষণ বোধ করছি না। এই কলকাতা শহরেই এক অরণ্যের মধ্যে বাস করছি ভাই।