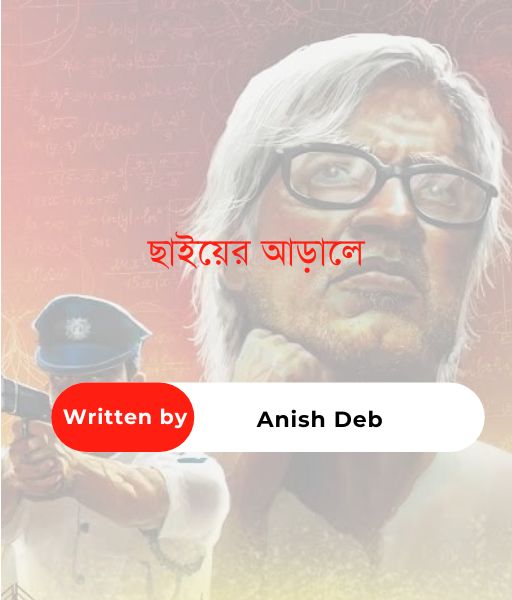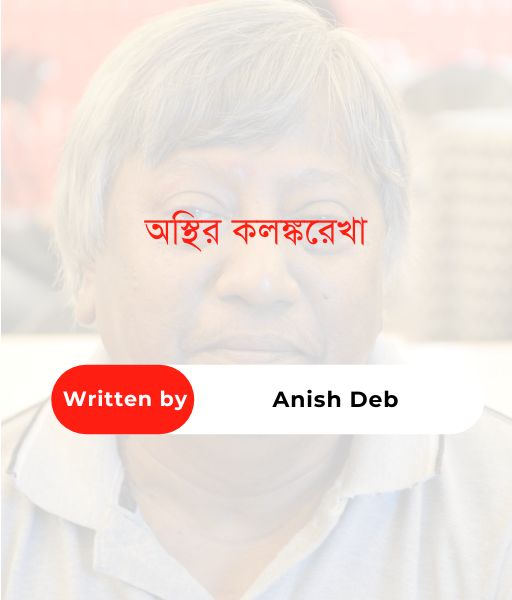অনির্বাণ ছাই
আমাকে নামিয়ে দিয়ে লজঝড়ে বাসটা ধুলো উড়িয়ে চলে গেল।
ধুলোর কুয়াশা ফিকে হলে চোখের সামনে যা দেখলাম তা যেন ফ্রেমে বাঁধানো ছবি। যেদিকে দু-চোখ যায় সেদিকেই টিয়াপাখি-রঙের ধানখেত। বিকেলের রোদ পড়ে ঝকঝক করছে। তারই মধ্যে কোথাও-কোথাও বড়-বড় গাছ। দু-একটা পাকা বাড়ি।
পিচের রাস্তা থেকে একটা চওড়া মোরাম বিছানো পথ ডানদিকে চলে গেছে। সেই পথের পাশে একটা বড় জামগাছ। অনির্বাণ এই গাছটার কথা বলেছিল। বলেছিল, ওই গাছের নীচে ও দাঁড়িয়ে থাকবে।
কিন্তু এতবছর পর ওকে কি আমি চিনতে পারব? ও-ও বোধহয় আমাকে চিনতে পারবে না। স্কুলে আমরা একসঙ্গে অনেক বছর পড়েছি বটে, কিন্তু স্কুল ছেড়েছি প্রায় বারো বছর হয়ে গেল। আমাদের দুজনের চেহারাই নিশ্চয়ই অনেক পালটে গেছে।
দেখলাম, গাছতলায় একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে। লোকটা রোগা, কালো, মাথার চুল উড়ছে, হাতে ভাঁজ করা একটা কালো ছাতা। এছাড়া ধু-ধু রাস্তায় আর কেউ নেই। দুটো গাঙশালিক পথের ধারে ঘাসঝোপের মধ্যে খেলা করছিল।
আমি হাঁটতে-হাঁটতে পকেট থেকে সেলফোন বের করলাম। অনির্বাণের নম্বর দেখে ডায়াল করলাম।
দেখলাম, গাছতলার লোকটা পকেট থেকে ওর সেল বের করে কানে দিল।
আমি কথা বললাম, ‘অনির্বাণ?’
‘হ্যাঁ। তুই অনির্বাণ?’
‘অফ কোর্স—অনির্বাণ নাম্বার ওয়ান।’
‘আমি তোর জন্যে গাছতলায় দাঁড়িয়ে আছি। তুই কোথায়?’
‘তোর দিকেই এগোচ্ছি—পায়ে হেঁটে…।’
এ-কথা যখন বললাম তখন আমাদের মধ্যে মাত্র হাতপাঁচেকের তফাত।
গাছের ছায়ার ভেতরে ঢুকে পড়ে আমি লোকটার একেবারে মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়ালাম। সেলফোন অফ করে পকেটে ঢুকিয়ে অবাক সুরে চেঁচিয়ে বললাম, ‘তুই অনির্বাণ দুই?’
লোকটা হেসে আমাকে বুকে জাপটে ধরো: ‘ঠিক বলেছিস। আজ কতবছর পরে একের সঙ্গে দুইয়ের দেখা হল বল তো! ভীষণ ভালো লাগছে রে—নতুন করে আবার বাঁচতে ইচ্ছে করছে।’
প্রথম আবেগের ঝাপটা কেটে গেলে হারানো বন্ধুর দিকে ভালো করে তাকালাম। ও-ও আমাকে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল।
স্কুলে আমাদের স্কুলে একটা বিরল ঘটনা ছিলাম আমরা দুজন। কারণ, আমাদের দুজনেরই নাম অনির্বাণ সরকার। তাই গুলিয়ে যাওয়ার সমস্যা এড়াতে স্কুলের স্যাররা কখন যেন আমাকে অনির্বাণ ওয়ান, আর ওকে অনির্বাণ টু করে দিয়েছিলেন। আমি মাথায় একটু বেশি লম্বা ছিলাম। হয়তো সেইজন্যেই ‘ওয়ান’ উপাধি পেয়েছিলাম। স্কুলের বন্ধুরা সংক্ষেপে আমাদের বলত ‘ওয়ান’ আর ‘টু’।
টু আমার চেয়ে মাথায় খাটো হলে কী হবে ওর মাথা—মানে, ব্রেন—ছিল নাম্বার ওয়ান। তা ছাড়া ওর রং ছিল টকটকে ফরসা, আর আমি তার ঠিক উলটো—একেবারে কেষ্ট ঠাকুর।
ক্লাসে আমাদের বন্ধুত্বটা কী করে যেন বেশ আঠালো হয়ে গিয়েছিল। মনের সব কথা আমি ওকে খুলে বলতাম। আর ও-ও আমাকে সব কথা খুলে বলত।
নীচু ক্লাসে থেকে ওপরে উঠতে-উঠতে আমরা এক সঙ্গে বড় হচ্ছিলাম। সুখ-দুঃখগুলোকে নতুন করে চিনতে পারছিলাম, আর সেগুলো দুজনে মিলে ভাগ করে নিচ্ছিলাম। সবমিলিয়ে দিনগুলো বেশ কাটছিল।
তারপর স্কুল একদিন ফুরোল। চলে এল এক আর দুইয়ের ছাড়াছাড়ির দিন। বেশ মনে আছে, সেদিন স্কুল ছুটির পরে আমরা দুজনে বোসদের পুকুরের ঘাটে গিয়ে বসেছিলাম। অনেক গল্প করেছিলাম। কেঁদেও ছিলাম।
আজও সব মনে আছে আমার।
তারপর কত মাস কত বছর যে কেটে গেছে! দুইয়ের কথা না ভুললেও স্মৃতির পাতা অনেকটা আবছা হয়ে এসেছিল। মনে-মনে শুধু চাইতাম ও যেখানেই থাক খুশিতে থাক, আনন্দের ধুলো মাখা থাক ওর কপালে। কারণ, অনির্বাণ বেশিরভাগ সময়েই খুব মনমরা হয়ে থাকত। আর একটু যেন চাপা স্বভাবের ছিল।
কলেজের পাট শেষ করে আমি যখন চাকরি করছি তখন আমাদেরই এক স্কুলের বন্ধু কমলেশের সঙ্গে হঠাৎ দেখা। ও বলল, ‘টু, ওয়ান তোকে ফোন করবে। কোত্থেকে যেন আমার ফোন নাম্বার জোগাড় করে আমাকে ফোন করেছিল। নেক্সট উইকে শনিবার ওর বিয়ে। আমাকে যেতে বলেছে। তোকে বলবে। তবে আমার বোধহয় যাওয়া হবে না। কোন ধ্যাড়ধেড়ে গোবিন্দপুর—মানে, আসনপুর না কেশবপুর—কোথায় যেন থাকে। যাকগে, তোকে ও ফোন করবে।’
অনির্বাণ আমাকে ফোন করেছিল। বিয়েতে নেমন্তন্নও করেছিল। কিন্তু আমার যাওয়া হয়নি। অফিসের কাজের চাপ আর কেশবপুরের দূরত্ব—এই দুটো ফ্যাক্টরই বাদ সেধেছিল।
বিয়েতে যাইনি বলে অনির্বাণ টু অভিমান করে আমাকে আর কখনও ফোন-টোন করেনি। আমিও সংকোচে ওকে ফোন করে উঠতে পারিনি।
এরপর বছর ছয়েক কেটে গেছে। ওর সঙ্গে আর যোগাযোগ হয়নি। কেমন একটা ‘কিন্তু-কিন্তু’ পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে সময়টা কেটে গেছে। তারপর হঠাৎই ওর ফোন এল। মাত্র তিনদিন আগে।
‘ওয়ান?’
‘হ্যাঁ—।’
‘টু বলছি।’
‘অনির্বাণ। কেমন আছিস? শোন, আমি এক্সট্রিমলি সরি। তোর বিয়েতে যেতে পারিনি রে। এমন কাজের প্রেশার পড়ল যে, কী আর বলব। আমি…।’
‘ওসব ফালতু কথা ছাড়, ওয়ান।’ আমাকে রুক্ষভাবে থামিয়ে দিল অনির্বাণ: ‘ওসব তো হাফডজন বছরের পুরোনো কথা। আজ খুব জরুরি দরকার তোকে ফোন করেছি। তোকে আমার বাড়িতে একবার আসতেই হবে। ভীষণ দরকার। কবে আসবি বল?
আমি ওকে আশ্বস্ত করার জন্যে বললাম, ‘যাব, যাব। কিন্তু তোর কী হয়েছে বল তো? তোর কথা শুনে তোকে ভীষণ আপসেট বলে মনে হচ্ছে…।’
‘তুই এলে সব বলব। তোর কাছে তো আমার গোপন কিছুই নেই! বল, কবে আসবি?’
একটু চিন্তা করে আমি বললাম, ‘পরশু যাব। তা তোর ফ্যামিলি লাইফ কেমন চলছে বল। ওয়াইফ কেমন আছে? ছেলেমেয়ে ক’টা?’
অনির্বাণ টু চুপ করে গেল। কয়েকসেকেন্ড পর একটু যেন বিষণ্ণ গলায় বলল, ‘ওদের নিয়েই তো প্রবলেম। ওয়াইফ…আর আমার চার বছরে ফুটফুটে মেয়েটা। তুই পরশু আয়, ওয়ান। আমাকে ঝোলাস না যেন! তুই এলে সব বলব। তোর হেলপ না পেলে আমার সর্বনাশ হবে…।’
আরও কয়েকটা কথার পর আমি শপথ করে বলছিলাম, ‘…পরশু বিকেলে তা হলে তোর সঙ্গে দেখা হচ্ছে। প্রমিস।’
‘থ্যাংকু ইউ, ভাই। আমি তোর জন্যে কেশবপুর মোড়ে জামগাছতলায় ওয়েট করব…।’
এখন জামগাছতলায় দাঁড়ানো লোকটাকে আমি খুঁটিয়ে দেখছিলাম। নাঃ, অনির্বাণ টু আগের চেয়ে অনেক কালো হয়ে গেছে। চেহারাও অনেক শুকিয়ে গেছে। এই বয়েসেই গাল বসে গেছে। ঠোঁট খসখসে। চোখগুলো বড় বেশি সাদাটে।
ও আমাকে বাড়ির পথ ধরে এগিয়ে নিয়ে চলল। আমি বারবার বারণ করা সত্ত্বেও ছাতাটা খুলে মাথার ওপরে ধরে রইল।
চওড়া রাস্তা ছেড়ে আমরা সরু পথে ঢুকে পড়লাম। দুপাশে বাঁশগাছ, জবাফুলের গাছ, ভেরেন্ডার বেড়া। কয়েকটা ছোট-ছোট ডোবা। সেখানে লুকোনো চুনোমাছ বুড়বুড়ি কাটছে।
পথে বেশ কয়েকটা কুঁড়েঘর চোখে পড়ল। বাখারির কাঠামোয় গোবর আর মাটির চাপান দেওয়া দেওয়াল। কোথাও-কোথাও মাটির চাঙড় খসে পড়েছে। সেই কুঁড়েঘরের ফাঁক দিয়ে কয়েকটা দোতলা বাড়ি দেখা যাচ্ছিল।
উঁচু-নীচু কাঁচা পথ পেরিয়ে একটা সমতল মাটির উঠোনে এসে দাঁড়ালাম। আরও একটু এগোতেই একটা মামুলি দোতলা বাড়ি। তার একটা অংশ পুড়ে কালচে হয়ে ধসে পড়েছে।
সেই বাড়িটার দিকে আঙুল দেখিয়ে অনির্বান টু বলল, ‘আয়, এটাই আমার বাড়ি। দেখেছিস, কীরকম ড্যামেজ হয়ে গেছে!’
পথে আসার সময় অনির্বাণ ওর স্ত্রী আর মেয়ের কথা বলছিল। কাঞ্চন আর কাঞ্চি। ওদের নিয়ে একসঙ্গে বেঁচে থাকাটাই একটা স্বপ্নের মতো। কী দারুণ জীবন! অনেক ভাগ্য করে মানুষ এরকম জীবন পায়। আরও কত ভালো-ভালো কথা।
ওর কথা শুনতে-শুনতে মনে হচ্ছিল এবার বাবা-মায়ের কথা মেনে নিয়ে বিয়েটা করে নিলেই হয়! স্বপ্নের মতো দারুণ জীবন তো সবাই চায়!
বাড়ির ভেতরে ঢুকতেই কেমন একটা পোড়া-পোড়া গন্ধ পেলাম। দুধ উথলে উনুনে পড়লে যেমন পোড়া গন্ধ বেরোয়।
আমি নাক টেনে গন্ধটা কোনদিক থেকে আসছে সেটা ঠাওর করতে চেষ্টা করছিলাম। অনির্বাণকে জিগ্যেস করলাম, ‘কী পুড়ছে রে?’
ও নির্লিপ্ত গলায় বলল, ‘আমার বাড়ি। বাড়িটা পুড়ছে।’
আমি ওর ঠাট্টার মানে বুঝতে না পেরে ওর মুখের দিকে তাকালাম। মনে হল মুখটা যেন বিষণ্ণ পাথর দিয়ে তৈরি।
বাড়িতে ঢুকে অনির্বাণ দোতলার সিঁড়ি দিকে এগোল। আমি বাধ্য অতিথির মতো ওর পিছু নিলাম। আমাদের পায়ের শব্দ কেমন যেন ফাঁপা প্রতিধ্বনি তুলছিল।
আমি কান পেতে কাঞ্চন বা কাঞ্চির গলার আওয়াজ শুনতে চাইলাম, কিন্তু পেলাম না। লক্ষ করলাম, যে-অনির্বাণ এতক্ষণ ধরে এত কথা বলছিল সে বাড়িতে ঢোকার পর থেকে কীরকম যেন চুপচাপ হয়ে গেছে।
আমরা দোতলায় উঠে এলাম।
সামনেই চওড়া বারান্দা। চকচকে লাল মেঝে। রেলিঙের ওপরে গ্রিল দেওয়া।
বারান্দার ডানদিকে একটা পোড়া দরজা। সেটা পেরিয়ে একটা ঘর। তার দেওয়ালগুলো কালো, ফাটল ধরা, কোথাও-কোথাও ধসে পড়েছে।
পোড়া গন্ধটা আরও তীব্র হয়ে নাকে ধাক্কা মারল।
সেই ঘরটার মধ্যে আমাকে নিয়ে ঢুকল অনির্বাণ। সঙ্গে-সঙ্গে পোড়া গন্ধটা শ্মশানের গন্ধ হয়ে গেল।
আমার চারপাশে পোড়া ক্যালেন্ডার, পোড়া দেওয়াল-ঘড়ি, পোড়া খাট-বিছানা, পোড়া জানলা, পোড়া আলনার জামাকাপড়, পোড়া ড্রেসিংটেবিল, আর পোড়া ফটোগ্রাফ।
আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে দৃশ্যটা দেখতে লাগলাম। বেশ কিছুক্ষণ মুখ দিয়ে কোনও কথা বেরোল না।
অনেকক্ষণ পর প্রায় ফিসফিস করে ওকে জিগ্যেস করলাম, ‘কবে হল?’
ও বলল, ‘হয়েছে। দাঁড়া, তোকে একটা জিনিস দেখাই। যে জন্যে তোকে এতদূর ডেকে এনেছি…।’
কথাগুলো বলতে-বলতেই ঘরটার আর-একটা পোড়া দরজা দিয়ে অনির্বাণ টু চট করে কোথায় চলে গেল।
আমার কেমন যেন অপ্রস্তুত লাগছিল। লোকের বাড়িতে এলে আগে লোক একটু জলখাবারের ব্যবস্থা করে, চা-টা দেয়—তারপর…। তার বদলে ও এসব কী করছে!
বাড়িটায় কোনও লোকজনের আওয়াজ নেই। চারপাশে পোড়া গন্ধ। ওর আচরণও কেমন অদ্ভুত। তা ছাড়া…।
একটা টিনের বাক্স হাতে ফিরে এল অনির্বাণ। বাক্সটা কালচে, তোবড়ানো। জুতোর বাক্সের চেয়ে মাপে খানিকটা বড়। দেখেই বোঝা যায় বাক্সটা অনেক পুরোনো।
অনির্বাণ বিষণ্ণ গলায় বলল, ‘ওয়ান, তোকে এটা দেব বলে এতদিন ওয়েট করেছি। স্কুলে তুই আর আমি ছিলাম যাকে বলে হরিহর আত্মা। তাই এটা আমি তোর জন্যে রেখেছি। তুই এটার একটা গতি না করলে আমি শান্তি পাচ্ছি না। প্লিজ, ওয়ান, তুই আমাকে এইটুকু হেলপ কর…।’
বাক্সটা ও আমার হাতে দিল। আমি ওর কথা শুনতে-শুনতে যেন হিপনোটাইজড হয়ে গিয়েছিলাম। রোবটের মতো হাত বাড়িয়ে বাক্সটা নিলাম।
বাক্সটা বেশ হালকা কিন্তু হাতে গরম ঠেকল। হাত পুড়ে যাওয়ার মতো নয়, কিন্তু বেশ গরম।
কী আছে বাক্সের ভেতরে?
সেই প্রশ্নটাই করলাম ওকে, ‘এর ভেতরে কী আছে রে?’
অনির্বাণ প্রশ্ন শুনে উসখুস করে উঠল। বারকয়েক মেঝের দিকে তাকাল। আঙুলে আঙুল ঠেকিয়ে নখের ডগা খুঁটতে লাগল।
‘কী আছে বলবি তো!’
একটু ইতস্তত করে ও বিড়বিড় করে বলল, ‘ওয়ান, কিছুদিন আগে আমার ফ্যামিলিতে একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়। আচমকা এই ঘরটায় আগুন লেগে যায়। আমি বাড়িতে ছিলাম না। তারকেশ্বরে একটা কাজে গিয়েছিলাম। ফিরে দেখি সব শেষ! কাঞ্চন…আর কাঞ্চি…আমার পুতুলের মতো ফুটফুটে মেয়েটা…ওরা আর নেই। আগুন…আগুন ওদের খেয়ে ফেলেছে…খেয়ে চেটেপুটে সব শেষ। শেষ!’ কথা বলতে-বলতে কেঁদে ফেলল অনির্বাণ।
‘সে কী রে! বলিস কী! আশপাশের কেউ কিছু করতে পারল না?’
মাথা নাড়ল অনির্বাণ: ‘নাঃ। কিছু করে ওঠার আগেই সব শেষ। সব জ্বলে-পুড়ে খাক।’
হঠাৎই ঘরের ভেতরটা আঁধার হয়ে এল। একইসঙ্গে মেঘের ডাক কানে এল।
অবাক হয়ে একটা জানলার দিকে তাকালাম।
আশ্চর্য! একটু আগেই খোলা জানলা দিয়ে একটা নারকেল গাছ আর বিকেলের রোদ দেখা যাচ্ছিল—এখন নারকেল গাছটা আছে, তবে রোদ লুকিয়ে পড়েছে। আর গাছটাও অস্পষ্ট, ভালো করে দেখা যাচ্ছে না।
অনির্বাণ দেওয়ালের পোড়া সুইচবোর্ডের দিকে হাত বাড়িয়ে বোধহয় একটা সুইচ টিপে দিল। সঙ্গে-সঙ্গে একটা বালব হলদেটে আলো ছড়িয়ে দিল ঘরে।
আমি ভয় পেয়ে গেলাম। পোড়া ঘর, বাইরের আঁধার, বালবের আলোয় তৈরি হওয়া কালো-কালো ছায়া, আর সামনে পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকা অন্যরকম অনির্বাণ আমাকে কেমন যেন ভয় পাইয়ে দিল।
‘কী আছে এই বাক্সের ভেতরে?’ ফাঁপা গলায় ওকে প্রশ্ন করলাম।
‘বাক্স খুলে দেখ…।’
আমার ভেতরে একটা জেদ তৈরি হচ্ছিল। ভয় পেলেও সেই জেদের জোরেই একটানে বাক্সের ঢাকনা খুলে ফেললাম।
বাক্স ভরতি কালো ছাই।
‘ওগুলো কাঞ্চন আর কাঞ্চির ছাই…।’ অনির্বাণ টু বলল।
আমি সম্মোহিতের মতো ছাইগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলাম।
‘এগুলো তুই গঙ্গায় ভাসিয়ে দিস…।’ ঠোঁট টিপে ও কান্না চাপতে চাইল। তারপর আর্ত সুরে বলল, ‘দিবি তো?’
আমি ঘাড় নেড়ে বললাম, ‘হ্যাঁ—দেব।’ তবে একইসঙ্গে ভাবছিলাম, ওর বউ আর মেয়ে কবে আগুনে পুড়ে মারা গেছে? ও বলছিল, ‘কিছুদিন আগে।’ তা হলে ছাইগুলো এখনও গরম থাকে কেমন করে?
আমার অবাক ভাবটা অনির্বাণের চোখে পড়ল। ও বলল, ‘ভাবছিস ছাইগুলো এখনও গরম আছে কেমন করে, তাই না? তা হলে শোন, ওই ছাইয়ের আগুন এখনও নেভেনি। এখনও আমি জ্বলে-পুড়ে শেষ হয়ে যাচ্ছি। আচ্ছা, তোর যদি এমন হত তুই কী করতিস? যদি তোর সবচেয়ে প্রিয় মানুষ দুজন এরকম আগুনে পুড়ে শেষ হয়ে যেত তা হলে তোর মনের অবস্থাটা কী হত? বল, সত্যি করে বল। একটিবার বল…।’
ওর প্রত্যাশা ভরা সজল চোখের দিকে তাকিয়ে আমার মায়া হল। কে যেন আমাকে দিয়ে আচমকা বলিয়ে নিল, ‘কিছু মনে করিস না। ওরকম হলে আমার আর বাঁচতে ইচ্ছে করত না…।’
‘ঠিক বলেছিস।’ তর্জনী তুলে উত্তেজিতভাবে সায় দিল অনির্বাণ। তাড়াতাড়ি কথা বলতে গিয়ে ওর জিভ জড়িয়ে গেল: ‘তাই কী করেছিলাম জানিস?’ কথাটা বলেই ও একছুটে ভেতরের দরজা পেরিয়ে কোথায় চলে গেল। কিন্তু প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই একটা প্লাস্টিকের জেরিক্যান হাতে আবার ঘরে ফিরে এল। ক্যানের ছিপি খুলতে-খুলতে বলল, ‘কেরোসিন নিয়ে নিজের গায়ে মাথায় ঢালতে শুরু করেছিলাম…’ জেরিক্যান উলটে পাগলের মতো নিজের শরীরে কেরোসিন ঢালতে লাগল ও। হাঁপাতে-হাঁপাতে বলতে লাগল, ‘এই যে—এইভাবে। এইভাবে…ঢালছিলাম…।’
কেরোসিনে ওর মাথার চুল ভিজে গেল। ভিজে গেল সারা শরীর, গায়ের জামাকাপড়। ঘরের মেঝেতে কেরোসিনের বন্যা বয়ে গেল। তীব্র গন্ধে চারদিক ভেসে গেল।
‘অনির্বাণ! অনির্বাণ! কী করছিস তুই?’ আমি ভয় পাওয়া গলায় চিৎকার করে উঠলাম।
আমার চিৎকার অনির্বাণ টু শুনতে পেল বলে মনে হল না। কেরোসিনের ক্যানটা ঝাঁকিয়ে-ঝাঁকিয়ে তরলের শেষ ফোঁটাটুকু পর্যন্ত নিজের গায়ে ঢেলে দিচ্ছিল।
‘…তারপর ছুটে রান্নাঘরের গিয়ে দেশলাইটা নিয়ে এলাম…’ কথা বলতে-বলতে ছুটে বেরিয়ে গেল ও। এবং কয়েকসেকেন্ডের মধ্যেই একটা দেশলাইয়ের বাক্স নিয়ে ফিরে এল। হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল, ‘তারপর…তারপর…।’
ফস করে দেশলাই জ্বলে উঠল। তার সঙ্গে জ্বলে উঠল অনির্বাণ। দাউদাউ আগুনে জ্বলে-পুড়ে খাক হতে লাগল।
হঠাৎই এক দমকা বাতাস কোথা থেকে যেন ছুটে এল। ঘরের ভেতরে পাগল করা ঝড় তুলল। সেই ঝড়ে আমার হাতে ধরা বাক্সের ছাই উড়তে লাগল। ছাইয়ের গুঁড়োয় তৈরি কালো মেঘ খ্যাপা মোষের মতো ঘরে বাতাসে দাপিয়ে বেড়াতে লাগল।
উড়ে বেড়ানো ছাইয়ের কালো কুয়াশা ভেদ করে জ্বলন্ত অনির্বাণকে দেখা যাচ্ছিল। ওর উজ্জ্বল শরীরটা শূন্যে ভেসে উঠে এপাশ-ওপাশ দুলতে লাগল। ওর যন্ত্রণায় ডুকরে ওঠা স্বর শোনা গেল: ‘ওদের ছেড়ে আমি পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিলাম রে। তাই…তাই…তোর হাতের ওই বাক্সের ভেতরে আমিও আছি। কাঞ্চন আর কাঞ্চির সঙ্গে মিশে আছি…মিশে আছি…। আর আজও জ্বলে-পুড়ে মারছি। ওই ছাইয়ের আগুন আজও নেভেনি রে…।’