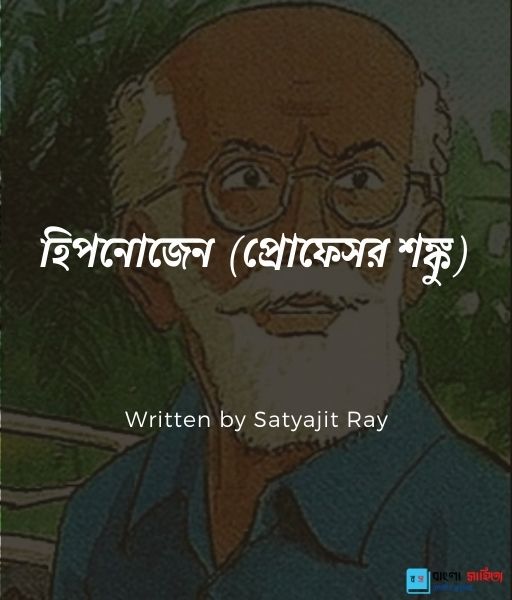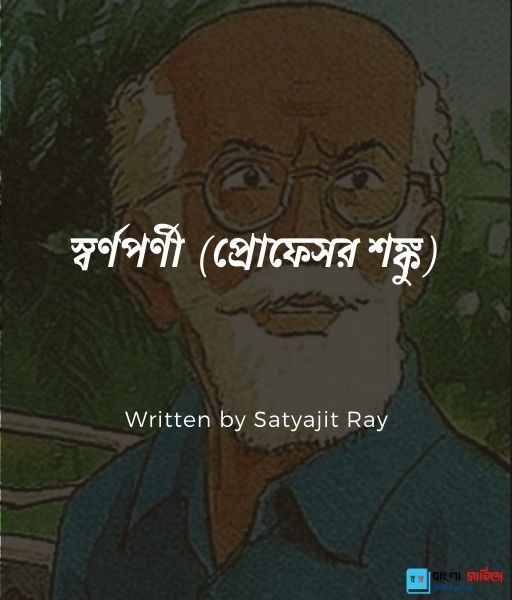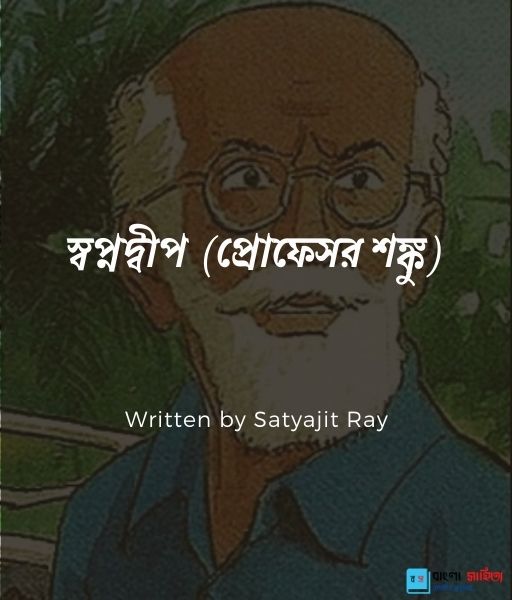ব্যোমযাত্রীর ডায়রি – ০১
প্রোফেসর ত্রিলোকেশ্বর শঙ্কুর ডায়রিটা আমি পাই তারক চাটুজ্যের কাছ থেকে।
একদিন দুপুরের দিকে আপিসে বসে পুজো সংখ্যার জন্য একটা লেখার প্রুফ দেখছি, এমন সময় তারকবাবু এসে একটা লাল খাতা আমার সামনে ফেলে দিয়ে বললেন, ‘পড়ে দেখো। গোল্ড মাইন।’
তারকবাবু এর আগেও কয়েকবার গল্পটল্প এনেছিলেন। খুব যে ভাল তা নয়; তবে বাবাকে চিনতেন, আর ছেঁড়া জামাটামা দেখে মনে হত, ভদ্রলোক বেশ গরিব; তাই প্রতিবারই লেখাগুলোর জন্য পাঁচ-দশ টাকা করে দিয়েছি।
এবারে গল্পের বদলে ডায়রিটা দেখে একটু আশ্চর্য হলাম।
প্রোফেসর শঙ্কু বছর পনেরো নিরুদ্দেশ। কেউ কেউ বলেন তিনি নাকি কী একটা ভীষণ এক্সপেরিমেণ্ট করতে গিয়ে প্রাণ হারান। আবার এও শুনেছি যে তিনি নাকি জীবিত; ভারতবর্ষের কোনও অখ্যাত অজ্ঞাত অঞ্চলে গা ঢাকা দিয়ে চুপচাপ নিজের কাজ করে যাচ্ছেন, সময় হলে আত্মপ্রকাশ করবেন। এ-সব সত্যিমিথ্যে জানি না, তবে এটা জানতাম যে তিনি বৈজ্ঞানিক ছিলেন। তাঁর যে ডায়রি থাকতে পারে সেটা অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু সে ডায়রি তারকবাবুর কাছে এল কী করে?
জিজ্ঞেস করতে তারকবাবু একটু হেসে হাত নাড়িয়ে আমার মশলার কৌটোটা থেকে লবঙ্গ আর ছোট এলাচ বেছে নিয়ে বললেন, ‘সুন্দরবনের সে ব্যাপারটা মনে আছে তো?’
এই রে আবার বাঘের গল্প। তারকবাবু তাঁর সব ঘটনার মধ্যে বাঘ জিনিসটাকে যেভাবে টেনে আনেন সেটা আমার মোটেই ভাল লাগে না। তাই একটু বিরক্ত হয়েই বললাম, ‘কোন ব্যাপারটার কথা বলছেন?’
‘উল্কাপার! ব্যাপার তো একটাই।’
ঠিক ঠিক। মনে পড়ছে। এটা সত্যি ঘটনা। কাগজে বেরিয়েছিল। বছরখানেক আগে একটা উল্কাখণ্ড সুন্দরবনের মাথারিয়া অঞ্চলে এসে পড়েছিল। বেশ বড় পাথর। কলকাতার জাদুঘরে যেটা আছে তার প্রায় দ্বিগুণ। মনে আছে, কাগজে ছবি দেখে হঠাৎ একটা কালো মড়ার খুলি বলে মনে হয়েছিল।
বললাম, ‘তার সঙ্গে এই খাতাটার কী সম্পর্ক?
তারকবাবু বললেন, ‘বলছি। ব্যস্ত হয়ো না। আমি গেসলাম ওই মওকায় যদি কিছু বাঘছাল জোটে। ভাল দর পাওয়া যায়, জান তো? আর ভাবলুম অত জন্তুজানোয়ার মোলো, তার মধ্যে কি গুটি চারেক বাঘও পড়ে থাকবে না? কিন্তু সে গুড়ে বালি। লেট হয়ে গেল। হরিণটরিণ কিচ্ছু নেই।’
‘তা হলে?’
‘ছিল কিছু গোসাপের ছাল। তাই নিয়ে এলুম। আর এই খাতাটা।’
একটু অবাক হয়ে বললাম, ‘খাতাটা কি ওইখানে…?’
‘গর্তের ঠিক মধ্যিখানে। পাথরটা পড়ায় একটা গর্ত হয়েছিল জান তো? তোমাদের চারখানা হেদো তার মধ্যে ঢুকে যায়। এটা ছিল তার ঠিক-মধ্যিখানে।’
‘বলেন কী!’
‘বোধহয় পাথরটা যেখানে পড়েছিল তার খুব কাছেই। লাল-লাল কী একটা মাটির ভেতর থেকে উঁকি মারছে দেখে টেনে তুললাম। তারপর খুলতেই শঙ্কুর নাম দেখে পকেটস্থ করলাম।’
‘উল্কার গর্তের মধ্যে খাতা? তার মানে কি…?’
‘পড়ে দেখো। সব জানতে পারবে। তোমরা তো বানিয়ে গল্পটল্প লেখো, আমিও লিখি। এ তার চেয়ে ঢের মজাদার। এ আমি হাতছাড়া করতাম না, বুঝলে! নেহাত বড় টানাটানি যাচ্ছে তাই–‘
ব্যোমযাত্রীর ডায়রি – ০২
টাকা বেশি ছিল না কাছে। তা ছাড়া ঘটনাটা পুরোপুরি বিশ্বাস হচ্ছিল না, তাই কুড়িটা টাকা দিলাম ভদ্রলোককে। দেখলাম তাতেই খুশি হয়ে আমায় আশীর্বাদ করে চলে গেলেন।
তার পর পুজোর গোলমালে খাতাটার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। এই সেদিন আলমারি খুলে চলন্তিকাটা টেনে বার করতে গিয়ে ওটা বেরিয়ে পড়ল।
খাতাটা হাতে নিয়ে খুলে কেমন যেন খটকা লাগল।
যতদূর মনে পড়ে প্রথমবার দেখেছিলাম কালির রং ছিল সবুজ। আর জা দেখছি লাল? এ কেমন হল?
খাতাটা পকেটে নিয়ে নিলাম। মানুষের তো ভুলও হয়। নিশ্চয়ই অন্য কোনও লেখার সবুজ কালির সঙ্গে গোলমাল করে ফেলেছি।
বাড়িতে এসে আবার খাতাটা খুলতেই বুকটা ধড়াস করে উঠল।
এবার দেখি কালির রং নীল।
তারপর এক অদ্ভুত ব্যাপার। দেখতে দেখতে চোখের সামনে নীলটা হয়ে গেল হলদে।
এবারে তো আর কোনও ভুল নেই; কালির রং সত্যি বদলাচ্ছে।
হাতের কাঁপুনিতে খাতাটা মাটিতে পড়ে গেল। আমার ভুলো কুকুরটা যা পায় তাতেই দাঁত বসায়। খাতাও বাদ গেল না। কিন্তু আশ্চর্য! যে দাঁত এই দু’ দিন আগেই আমার নতুন তালতলার চটিটা ছিঁড়েছে, ওই খাতার কাগজ তার কামড়ে কিচ্ছু হল না।
হাত দিয়ে টেনে দেখলাম এ কাগজ ছেঁড়া মানুষের সাধ্যি নয়।
টানলে রবারের মতো বেড়ে যাচ্ছে, আর ছাড়লে যে-কে-সেই।
কী খেয়াল হল, একটা দেশলাই জ্বেলে কাগজটায় ধরালাম। পুড়ল না। খাতাটা পাঁচ ঘণ্টা উনুনের মধ্যে ফেলে রেখে দিলাম। কালির রং যেমন বদলাচ্ছিল, বদলাল, কিন্তু আর কিচ্ছু হল না।
সেই দিনই রাত্রে ঘুমটুম ভুলে গিয়ে তিনটে অবধি জেগে খাতাটা পড়া শেষ করলাম। যা পড়লাম তা তোমাদের হাতে তুলে দিচ্ছি। এ সব সত্যি কি মিথ্যে, সম্ভব কি অসম্ভব, তা তোমরা বুঝে নিও।
১লা জানুয়ারি
আজ দিনের শুরুতেই একটা বিশ্রী কাণ্ড ঘটে গেল।
রোজকার মতো আজও নদীর ধারে মর্নিং ওয়াক সেরে ফেলেছি। শোবার ঘরে ঢুকতেই একটা বিদঘুটে চেহারার লোকের সামনে পড়তে হল। চমকে গিয়ে চিৎকার করেই বুঝতে পারলাম যে ওটা আসলে আয়না, এবং লোকটা আর কেউ নয়–আমারই ছায়া। এ ক’বছরে আমার চেহারা ওই রকম হয়েছে। আমার আয়নার প্রয়োজন হয় না বলে ওটার ওপর কালেন্ডারটা টাঙিয়ে রেখেছিলাম; আজ সকালেই বোধহয় প্রহ্লাদটা বছর শেষ হয়ে গেছে বলে সর্দারি করে ওটাকে নামিয়ে রেখেছে। ওকে নিয়ে আর পারা গেল না। সাতাশ বছর ধরে আমার সঙ্গে থেকে আমার কাজ করেও ওর বুদ্ধি হল না। আশ্চর্য!
চিৎকার শুনে প্রহ্লাদ ঘরে এসে পড়েছিল। ওকে একটু শিক্ষা দেওয়া দরকার মনে করে আমার Snuff-gun বা নস্যস্ত্রটা ওর ওপর পরীক্ষা করা গেল। দেখলাম, এ নস্যির যা তেজ, তাক করে গোঁফের কাছাকাছি মারতে পারলেই যথেষ্ট কাজ হয়! এখন রাত এগারোটা। ওর হাঁচি এখনও থামেনি। আমার হিসেব যদি ঠিক হয় তো তেত্রিশ ঘণ্টার আর ও হাঁচি থামবে না।
২রা জানুয়ারি
রকেটটা নিয়ে যে চিন্তাটা ছিল, ক্রমেই সেটা দূর হচ্ছে। যাবার দিন যত এগিয়ে আসছে, ততই মনে জোর পাচ্ছি, উৎসাহ পাচ্ছি।
এখন মনে হচ্ছে যে প্রথমবারের কেলেঙ্কাঋটার জন্য একমাত্র প্রহ্লাদই দায়ী। ঘড়িটায় দম দিতে গিয়ে সে যে ভুল করে কাঁটাটাই ঘুরিয়ে ফেলেছে তা আর জানব কী করে। এক সেকেণ্ড এ দিক ও দিক হলেই এ সব কাজ পণ্ড হয়ে যায়। আর কাঁটা ঘোরানোর ফলে আমার হয়ে গেল প্রায় সাড়ে তিনঘণ্টা লেট। রকেট যে খানিকটা উঠেই গোঁৎ খেয়ে পড়ে যাবে তাতে আর আশ্চর্য কী?
রকেট পড়ায় অবিনাশবাবুর মুলোর ক্ষেত নষ্ট হওয়ার দরুন ভদ্রলোক পাঁচশো টাকা ক্ষতিপূরণ চাইছেন। একেই বলে দিনে ডাকাতি। এ দিকে এত বড় একটা প্রচেষ্টা যে ব্যর্থ হতে চলেছিল তার জন্য কোনও আক্ষেপ বা সহানুভূতি নেই।
এই সব লোককে জব্দ করার জন্য একটা নতুন কোনও অস্ত্রের কথা ভাবা দরকার।
৫ই জানুয়ারি
প্রহ্লাদটা বোকা হলেও ওকে সঙ্গে নিলে হয়তো সুবিধে হবে। আমি মোটেই বিশ্বাস করি না যে এই ধরনের অভিযানে কেবলমাত্র বুদ্ধিমান লোকেরই প্রয়োজন। অনেক সময় যাদের বুদ্ধি কম হয় তাদের সাহস বেশি হয়, কারণ ভয় পাবার কারণটা ভেবে বের করতেও তাদের সময় লাগে।
প্রহ্লাদ যে সাহসী সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। সে বার যখন কড়িকাঠ থেকে একটা টিকটিকি আমার বাইকর্নিক অ্যাসিডের শিশিটার উপর পড়ে সেটাকে উলটে ফেলে দিন, তখন আমি সামনে দাঁড়িয়ে থেকেও কিছু করতে পারছিলাম না। স্পষ্ট দেখছি অ্যাসিডটা গড়িয়ে গড়িয়ে প্যারাডক্সাইট পাউডারের স্তুপটার দিকে চলেছে, কিন্তু দুটোর কনট্যাক্ট হলে যে কী সাংঘাতিক ব্যাপার হবে তাই ভেবেই আমার হাত পা অবশ হয়ে আসছে।
এমন সময় প্রহ্লাদ ঢুকে কাণ্ডকারখানা দেখে এক গাল হেসে হাতের গামছাটা দিয়ে অ্যাসিডটা মুছে ফেলল। আর পাঁচ সেকেণ্ড দেরি হলেই আমি, আমার ল্যাবরেটরি, বিধুশেখর, প্রহ্লাদ, টিকটিকি এ সব কিছুই থাকত না।
তাই ভাবছি হয়তো ওকে নেওয়াই ভাল। ওজনেও কুলিয়া যাবে। প্রহ্লাদ হল দু’মন সার সের, আমি এক মন এগারো সের, বিধুশেখর সাড়ে পাঁচ মন, আর জিনিসপত্তর সাজসরঞ্জাম মিলিয়ে মন পাঁচেক। আমার রকেটে কুড়ি মন পর্যন্ত জিনিস নির্ভয়ে নেওয়া চলতে পারে।
৬ই জানুয়ারি
আমার রকেটের পোষকটার আস্তিনে কতগুলো উচ্ছিংড়ে ঢুকেছিল, আজ সকালে সেগুলো ঝেড়েঝুড়ে বার করছি, এমন সময় অবিশানবাবু এসে হাজির। বললেন, ‘কী মশাই, আপনি তো চাঁদপুর না মঙ্গলপুর কোথায় চললেন। আমার টাকাটার কী হল?’
এই অবিনাশবাবুর রসিকতার নমুনা। বিজ্ঞানের কথা উঠলেই ঠাট্টা আর ভাঁড়ামো। রকেটটা যখন প্রথম তৈরি করছি তখন একদিন এসে বললেন, ‘আপনার ওই হাউইটা এই কালীপুজোর দিনে ছাড়ুন না। ছেলেরা বেশ আমোদ পাবে!’
এক-এক সময় মনে হয় যে পৃথিবীটা যে গোল, এবং সেটা যে ঘুরতে ঘুরতে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে সেটাও বোধহয় অবিনাশবাবু বিশ্বাস করেন না।
যাই হোক; আজ আমি তাঁর ঠাট্টায় কান না দিয়ে বরং উলটে তাঁকে খুব খাতির টাতির করে বসতে বললাম। তারপর প্রহ্লাদকে বললাম চা আনতে। আমি জানতাম যে অবিনাশবাবু চায়ে চিনির বদলে স্যাকারিন খান। আমি স্যাকারিনের বদলে ঠিক সেই রকমই দেখতে একটা বড়ি তাঁর চায়ে ফেলে দিলাম। এই বড়িই হল আমার নতুন অস্ত্র। মহাভারতের জৃম্ভণাস্ত্র থেকেই আইডিয়াটা এসেছিল, কিন্তু এটায় যে শুধু হাই উঠবে তা নয়। হাই-এর পর গভীর ঘুম হবে, এবং ঘুমের মধ্যে সব অসম্ভব ভয়ঙ্কর রকমের স্বপ্ন দেখতে হবে।
আমি নিজে কাল চার ভাগের এক ভাগ বড়ি ডালিমের রসে ডাইলিউট করে খেয়ে দেখেছি। সকালে উঠে দেখি স্বপ্ন দেখে ভয়ের চোটে দাড়ির বাঁ দিকটা একেবারে পেকে গেছে।
৮ই জানুয়ারি
নিউটনকে সঙ্গে নেব। ক’ দিন ধরেই আমার ল্যাবরেটরির আশেপাশে ঘোরাঘুরি করছে এবং করুণস্বরে ম্যাও ম্যাও করছে। বোধহয় বুঝতে পারছিল যে আমার যাবার সময়ে আসছে।
কাল ওকে Fish Pillটা খাওয়ালাম। মহা খুশি।
আজ মাছের মুড়ো আর বড়ি পাশাপাশি রেখে পরীক্ষা করে দেখলাম। ও বাড়িটাই খেল। আর কোনও চিন্তা নেই! এবার চটপট ওর জন্য একটা পোশাক আর হেলমেট তৈরি করে ফেলতে হবে।
১০ই জানুয়ারি
দু’ দিন থেকে দেখছি বিধুশেখর মাঝে মাঝে একটা গাঁ গাঁ করছে। এটা খুবই আশ্চর্য, কারণ বিধুশেখরের তো শব্দ করার কথা নয়। কলকব্জার মানুষ কাজ করতে বললে চুপচাপ কাজ করবে; এক নড়াচড়ায় যা ঠং ঠং শব্দ। ও তো আমারই হাতের তৈরি, তাই আমি জানি ওর কতখানি ক্ষমতা। আমি জানি ওর নিজস্ব বুদ্ধি বা চিন্তাশক্তি বলে কিছু থাকতেই পারে না। কিন্তু বেশ কিছুদিন থেকেই মাঝে মাঝে এর ব্যতিক্রম লক্ষ করছি।
এক দিনের ঘটনা খুব বেশি করে মনে পড়ে।
আমি তখন সবে রকেটের পরিকল্পনাটা করছি। জিনিসটা যে কোনও সাধারণ ধাতু দিয়ে তৈরি হতে পারে না, সেটা প্রথমেই বুঝেছিলাম। অনেক এক্সপেরিমেণ্ট করার পর, ব্যাঙের ছাতা, সাপের খোলস আর কচ্ছপের ডিমের খোলা মিশিয়ে একটা কমপাউণ্ড তৈরি করেছি, এবং বেশ বুঝতে পারছি যে এবার হয় ট্যানট্রাম বোরো প্যাক্সিনেট, না-হয় একুইয়স্ ভেলোসিলিকা মেশালেই ঠিক জিনিসটা পেয়ে যাব।
প্রথমে ট্যানট্রামটাই দেখা যাক ভেবে এক চামচ ঢালতে যাব এমন সময়ে ঘরে একটা প্রচণ্ড ঘটাং ঘটাং শব্দ আরম্ভ হল। চমকে গিয়ে পিছন ফিরে দেখি বিধুশেখরের লোহার মাথাটা ভীষণভাবে এপাশ-ওপাশ হচ্ছে এবং তাতে আওয়াজ হচ্ছে। খুব জোর দিয়ে বারণ করতে গেলে মানুষে যেভাবে মাথা নাড়ে ঠিক সেই রকম।
কী হয়েছে দেখতে যাব মনে করে ট্যানট্রামটা যেই হাত থেকে নামিয়েছি অমনি মাথা নাড়া থেমে গেল।
কাছে গিয়ে দেখি কোনও গোলমাল নেই। কলকব্জা তেলটেল সবই ঠিক আছে। টেবিলে ফিরে এসে আবার যেই ট্যানট্রামটা হাতে নিয়েছি অমনি আবার ঘটাং ঘটাং। এ তো ভারী বিপদ! বিধুশেখর কি সত্যিই বারণ করছে নাকি?
এবার ভেলোসিলিকাটা হাতে নিলাম। নিতেই আবার শব্দ। কিন্তু এবার মাথা নড়ছে উপর নীচে ঠিক যেমন করে মানুষে হ্যাঁ বলে।
শেষ পর্যন্ত ভেলোসিলিকা মিশিয়েই ধাতুটা তৈরি হল।
পরে ট্যানট্রামটা দিয়েও পরীক্ষা করে দেখেছিলাম। না করলেই ভাল ছিল। সেই চোখ-ধাঁধানো সবুজ আলো আর বিস্ফোরণের বিকট শব্দ কোনওদিন ভুলব না।
১১ই জানুয়ারি
আজ বিধুশেখরের কলকব্জা খুলে ওকে খুব ভাল করে পরীক্ষা করেও ওর আওয়াজ করার কোনও কারণ খুঁজে পেলাম না। তবে এও ভেবে দেখলাম যে এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। আমি আগেও অনেকবার দেখেছি যে আমার বৈজ্ঞানিক বিদ্যেবুদ্ধি দিয়ে আমি যে জিনিস তৈরি করি, সেগুলো অনেক সময়েই আমার হিসেবের বেশি কাজ করে। তাতে এক এক সময় মনে হয়েছে যে হয়তো বা কোনও অদৃশ্য শক্তি আমার অজ্ঞাতে আমার উপর খোদকারি করছে। কিন্তু সত্যিই কি তাই? বরঞ্চ আমার মনে হয় যে আমার ক্ষমতার দৌড় যে ঠিক কতখানি তা হয়তো আমি নিজেই বুঝতে পারি না। খুব বড় বড় বৈজ্ঞানিকদের শুনেছি এ রকম হয়।
আর একটা কথা আমার প্রায়ই মনে হয়। সেটা হচ্ছে, বাইরের কোনও জগতের প্রতি আমার যেন একটা টান আছে, এই টানটা লিখে বোঝানো শক্ত। মাধ্যাকর্ষণের ঠিক উলটো কোনও শক্তি যদি কল্পনা কর আযায়, তা হলে এটার আন্দাজ পাওয়া যাবে। মনে হয় যেন পৃথিবীর প্রভাব ছাড়িয়ে যদি কিছুদূর উপরে উঠতে পারি, তা হলেই এই টানটা আপনা থেকেই আমাকে অন্য কোনও গ্রহে টহে নিয়ে গিয়ে ফেলবে।
এ টানটা যে চিরকাল ছিল তা নয়। একটা বিশেষ দিন থেকে এটা আমি অনুভব করে আসছি। সেই দিনটার কথা আজো মনে আছে।
বারো বছর আগে। আশ্বিন মাস। আমি আমার বাগানে, একটা আরামকেদারায় শুয়ে শরৎকালের মৃদু মৃদু বাতাস উপভোগ করছি। আশ্বিন-কার্তিক মাসটা আমি রোজ রাত্রে খাবার পরে তিন ঘণ্টা এই ভাবে শুয়ে থাকি, কারণ এই দুটো মাসে উল্কাপাত হয় সবচেয়ে বেশি। এক ঘণ্টায় অন্তত আট-দশটা উল্কা রোজই দেখা যায়। আমার দেখতে ভারী ভাল লাগে।
সে দিন কতক্ষণ শুয়ে ছিলাম খেয়াল নেই হঠাৎ একটা উল্কা দেখলাম যেন একটু অন্য রকম। সেটা ক্রমশ বড় হচ্ছে, এবং মনে হল যেন আমার দিকেই আসছে। আমি একদৃষ্টে চেয়ে রইলাম। উল্কাটা ক্রমে ক্রমে কাছে এসে আবার বাগানের পশ্চিম দিকের গোলজ্ঞ গাছটার পাশে থেমে একটা প্রকাণ্ড জোনাকির মতো জ্বলতে লাগল। সে এক আশ্চর্য দৃশ্য!
আমি উল্কাটাকে ভাল করে দেখবে বলে চেয়ার ছেড়ে উঠে যেতেই আমার ঘুমটা ভেঙে গেল।
এটাকে স্বপ্ন বলেই বিশ্বাস করতাম, কিন্তু দুটো কারোনে খটকা রয়ে গেল। এক হল এই আকর্ষণ, যেটার বশে আমি তার পরদিন থেকেই রকেটের বিষয় ভাবতে শুরু করি।
আরেক হল এই গোলঞ্চ গাছ। সেই দিন থেকেই গাছটাতে গোলঞ্চর বদলে একটা নতুন রকমের ফুল হচ্ছে। এ রকম ফুল কেউ কোথাও দেখেছে কি না জানি না। আঙুলের মতো পাঁচটা করে ঝোলা ঝোলা পাপড়ি। দিনেরবেলা কুচকুচে কালো কিন্তু রাত হলেই ফসফরাসের মতো জ্বলতে থাকে। আর যখন হাওয়ায় দোলে তখন ঠিক মনে হয় যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে।
১২ই জানুয়ারি
কাল ভোর পাঁচটার মঙ্গলযাত্রা।
আজ প্রহ্লাদকে ল্যাবরেটরিতে ডেকে এনে ওর পোষাক আর হেলমেটটা পরিয়ে দেখলাম। ও তো হেসেই অস্থির। সত্যি কথা বলতে কী আমারও ওর চেহারা ও ভাবভাব দেখে হাসি পাচ্ছিল। এমন সময় একটা ঠং ঠং ঘং ঘং শব্দ শুনে দেখি বিধুশেখর তার লোহার চেয়ারটায় বসে দুলছে আর গলা দিয়ে একটা নতুন রকম শব্দ করছে। এই শব্দের মানে একটাই হতে পারে। বিধুশেখর প্রহ্লাদকে দেখে হাসছিল।
নিউটন হেলমেটটা পরানোর সময় একটু আপত্তি করছিল। এখন দেখছি বেশ চুপচাপ আছে, আর মাঝে মাঝে জিভ বার করে হেলমেটের কাচটা চেটে চেটে দেখছে।
২১শে জানুয়ারি
আমরা সাত দিন হল পৃথিবী ছেড়েছি। এ বার যাত্রায় কোনও বাধা পড়েনি। ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় রওনা হয়েছি।
যাত্রী এবং মালপত্র নিয়ে ওজন হল পনেরো মন বত্রিশ সের তিন ছটাক। পাঁচ বছরের মতো রসদ আছে সঙ্গে। নিউটনের এক-একটা Fish Pill-এ সাত দিনের খাওয়া হয়ে যায়। আমার আর প্রহ্লাদের জন্য বটফলের রস থেকে যে বড়িটা তৈরি করেছিলাম–বটিকা-ইণ্ডিকা–কেবল মাত্র সেইটাই নিয়েছি। বটিকা-ইণ্ডিকার একটা হ্যোমিওপ্যাথিক বড়ি খেলেই পুরো চব্বিশ ঘণ্টার জন্য খিদে তেষ্টা মিটে যায়। এক মন বড়ি সঙ্গে আছে।
নিউটনের এর ছোট জায়গায় বেশিক্ষণ বন্ধ থেকে অভ্যাস নেই তাই বোধ হয় প্রথম ক’ দিন একটু ছটফট করেছিল। কাল থেকে দেখছি আমার টেবিলের উপর বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাহিরের দৃশ্য দেখছে। কুচকুচে কালো আকাশ, তার মধ্যে অগণিত জ্বলন্ত গ্রহনক্ষেত্র। নিউটন দেখে আর মাঝে মাঝে আস্তে লেজের ডগাটা নাড়ে। ওর কাছে বোধ হয় অগুলোকে অসংখ্য বেড়ালের চোখের মতো মনে হয়।
বিধুশেখরের কোনও কাজকর্ম নেই, চুপচাপ বসে থাকে। ওর মন বা অনুভূতি বলে যদি কিছু থেকেও থাকে সেটা ওর গোল গোল বলের মতো নিষ্পলক কাচের চোখ দেখে বোঝবার কোনও উপায় নেই। প্রহ্লাদের দেখছি বাইরের দৃশ্য সম্পর্কে কোনও কৌতূহলই নেই, ও বসে বসে কেবলমাত্র রামায়ণ পড়ে। ভাগ্যে বাংলাটা শিখেছিল আমার কাছে।
২৫শে জানুয়ারি
বিধুশেখরকে বাংলা শেখাচ্ছি। বেশ সময় লাগবে বলে মনে হচ্ছে, তবে চেষ্টা আছে। প্রহ্লাদ যে ওর উচ্চারণের ছিরি দেখে হাসে, সেটা ও মোটেই পছন্দ করে না। দু-একবার দেখেছি ও মুখ দিয়ে গঁ গঁ আওয়াজ করছে আর পা দুটো ঠং ঠং করে মাটিতে ঠুকছে। ওর লোহার হাতের একটা বাড়ি খেলে যে কী দশ হবে সেটা কি প্রহ্লাদ বোঝে না?
আজ বিধুশেখরকে পরীক্ষা করবার জন্য জিজ্ঞেস করলাম, ‘কেমন লাগছে?’
ও প্রশ্নটা শুনে দু-তিন সেকেণ্ড চুপ করে থেকে হঠাৎ দুলতে আরম্ভ করল, কিছুক্ষণ সামনে পিছনে দুলে তারপর হাত দুটোকে পরস্পরের কাছে এনে ঠং ঠং করে তালির মতো বাজাল। দু-পায়ে খানিকটা সোজা হয়ে উঠে ঘাড়টাকে চিত করে বলল, ‘গাগোঃ’।
ও যে আসলে বলতে চাচ্ছিল, ‘ভাল’ সে বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নেই।
আজ মঙ্গলগ্রহটাকে একটা বাতাবিলেবুর মত দেখাচ্ছে। আমার হিসেব অনুযায়ী আরেক মাস পরে ওখানে পৌঁছব। এই ক’ মাস নির্বিঘ্নে কেটেছে। প্রহ্লাদ রামায়ণ শেষ করে মহাভারত ধরেছে।
আজ সকালে দূরবিন দিয়ে গ্রহটাকে দেখছি। এমন সময় খেয়াল হল বিধুশেখর কী জানি বিড়বিড় করছে। প্রথমে মন দিইনি, তারপর লক্ষ্য করলাম যে বেশ লম্বা একটা কথা বারবার বলছে। প্রতিবার একই কথা। আমি সেটা খাতায় নোট করে নিলাম, এই রকম দাঁড়াল।
‘ঘঙো ঘাংঙ কুঁক্ক ঘঙা আগাঁকেকেই ককুং খঙা।’
লেখাটা পড়ে এবং ওর কথা শুনতে শুনতে হঠাৎ বুঝতে পারলাম ও কী বলছে। কিছুদিন আগে দ্বিজু রায়ের একটা গান গুনগুন করে গাইছিলাম, এটা তারই প্রথম লাইন–‘ধনধান্য পুষ্প ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা’।
বিধুশেখরের উচ্চারণের প্রশংসা করতে না পারলেও ওর স্মরনশক্তি দেখে অবাক হয়ে গেলাম।
ব্যোমযাত্রীর ডায়রি – ০৩
জানালা দিয়ে এখন মঙ্গলগ্রহ ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। আস্তে আস্তে গ্রহের গায়ের রেখাগুলি স্পষ্ট হয়ে আসছে। কাল এই সময়ে ল্যাণ্ড করব। অবিনাশবাবুর ঠাট্টার কথা মনে পড়লে হাসি পায়। আমাদের যে সমস্ত জিনিস সঙ্গে নিয়ে নামতে হবে সেগুলো গুছিয়ে রেখেছি–ক্যামেরা, দূরবিন, অস্ত্রশস্ত্র, ফার্স্ট-এড বক্স, এ সবই নিতে হবে।
মঙ্গলগ্রহে যে প্রাণী আছে, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই। তবে তারা যে কী রকম–ছোট কি বড়, হিংস্র না অহিংস–তা জানি না। একেবারে মানুষের মতো কিছু হবে সেটাও অসম্ভবন বলে মনে হয়। যদি বিদঘুটে কোনও প্রাণী হয় তা হলে প্রথমটা ভয়ের কারণ হতে পারে পারে। কিন্তু এটা মনে রাখা দরকার যে আমরা যেমন তাদের কখনও দেখিনি, তারাও কখনও মানুষ দেখেনি।
প্রহ্লাদকে দেখলাম তার ভয়-ভাবনা নেই। সে দিব্যি নিশ্চিন্ত আছে। তার বিশ্বাস গ্রহের নাম যখন মঙ্গল তখন সেখানে কোনও অনিষ্ট হতেই পারে না। আমিও ওর সরল বিশ্বাসে–
তখন ডায়েরি লিখতে লিখতে এক কাণ্ড হয়ে গেল। বিধুশেখরকে ক’ দিন থেকেই একটু চুপচাপ দেখছিলাম কেন। তা ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। এখনও প্রশ্ন করলে ঠিক উত্তর দিতে পারে না। কেবল কোনও একটা কথা বললে সেটা শুনে নকল করার চেষ্টা করে।
আজ চুপচাপ বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ কী যে হল এক লাফে যন্ত্রপাতির বোর্ডটার কাছে গিয়ে উঠে যে হ্যাণ্ডেলটা টানলে রকেটটা উলটো দিতে যায় সেইটা ধরে প্রচণ্ড টান। আমরা তো ঝাঁকুনির চোটে সব কেবিনের মেঝেয় গড়াগড়ি।
কোনও মতে উঠে গিয়ে বিধুশেখরের কাঁধের বোতামটা টিপতেই ও বিকল হাত-পা মুড়ে পড়ে গেল। তারপর হ্যাণ্ডেল ঘুরিয়ে মোড় ফিরিয়ে আবার মঙ্গলের দিকে যাত্রা।
বিধুশেখরের এরকম পাগলামির কারণ কী? ওকে আপাতত অকেজো করেই রেখে দেব। ল্যাণ্ড করবার পর আবার বোতাম টিপে চালু করব। আমার বিশ্বাস ওর ‘মনের’ উপর চাপ পড়ছিল বেশ, বড্ড বেশি কথা বলা হয়েছে ওর সঙ্গে, তাই বোধহয় ওর ‘মাথাটা’ বিগড়ে গিয়েছিল।
আর পাঁচ ঘণ্টা আছে আমাদের ল্যাণ্ড করিতে। গ্রহের গায়ে যে নীল জায়গাগুলো প্রথমে জল বলে মনে হয়েছিল, সেটা এখন অন্য কিছু বলে মনে হচ্ছে। সরু সরু লাল সুতোগুলো যে কী এখনও বুঝতে পারছি না।
আমরা দু’ ঘণ্টা হল মঙ্গলগ্রহে নেমেছি। একটা হলদে রঙের নরম ‘পাথরের’ ঢিবির উপরে বসে আমি ডায়রি লিখছি। এখানে গাছপালা মাটি পাথর সবই কেমন জানি নরম রবারের মতো।
সামনেই হাত বিশেক দূরে একটা লাল নদী বয়ে যাচ্ছে। সেটাকে প্রথমে নদী বলে বুঝিনি কারণ ‘জল’টা দেখলে ঠিক মনে হয় যেন স্বচ্ছ পেয়ারার জেলি। এখান সব নদীই বোধহয় লাল। এবং সেগুলোকেই আকাশ থেকে লাল সুতোর মতো দেখায়। যেটাকে রকেট থেকে জল বলে মনে হয়েছিল সেটা আসলে ঘাস আর গাছপালা–সবই সবুজের বদলে নীল। আকাশের রং কিন্তু সবুজ, তাই সব কী রকম উলটো মনে হয়।
এখন পর্যন্ত কোনও প্রাণী চোখে পড়েনি। আমার হিসেব তা হলে ভুল হল নাকি? কোনও সাড়াশব্দও পাচ্ছি না? কেমন যেন একটা থমথমে ভাব। এক নদীর জলের কুলকুল শব্দ ছাড়া আর কোনও শব্দই নেই; আশ্চর্য নিস্তব্ধ।
ঠাণ্ডা নেই; বরঞ্চ গরমের দিকে। কিন্তু মাঝে মাঝে এক একটা হাওয়া আসে, সেটা ক্ষণস্থায়ী হলেও একেবারে হাড় পর্যন্ত কাঁপিয়ে দেয়। দূরের হয়তো বরফের পাহাড় টাহাড় জাতীয় কিছু আছে।
নদীর জলটা প্রথমে পরীক্ষা করতে সাহস পাচ্ছিলাম না। তারপর নিউটনকে খেতে দেখে ভরসা পেলাম। আঁজলা করে তুলে দেখে দেখি অমৃত! মনে পড়ল একবার গারো পাহাড়ে একটা ঝরনার জল খেয়ে আশ্চর্য ভাল লেগেছিল। কিন্তু এর কাছে সে জল কিছুই না। এক ঢোঁক খেয়েই শরীর ও মনের সমস্ত ক্লান্তি দূর হয়ে গেল।
বিধুশেখরকে নিয়ে আজ এক ফ্যাসাদ। ওর যে কী হয়েছে জানি না। রকেট ল্যাণ্ড করার পর বোতাম টিপে ওকে চালু করে দিলাম, কিন্তু নড়েও না চড়েও না। জিজ্ঞেস করলাম, ‘কী হয়েছে, তুমি নামবে না?’
ও মাথা নেড়ে না বলল।
বললাম, ‘কেন, কী হয়েছে?’
এবার বিধুশেখর হাত দুটো মাথার উপর তুলে গম্ভীর ভয়-পাওয়া গলায় বলল, ‘বিভং’।
বিধুশেখরের ভাষা বুঝতে আমার কোনও অসুবিধা হয় না। তাই বুঝলাম ও বলছে, ‘বিপদ’। জিজ্ঞেস করলাম, ‘কী বিপদ বিধুশেখর? কীসের ভয়?’
বিধুশেখর আবার গম্ভীর গলায় বলল, ‘বিভং ভীবং বিভং’।
বিপদ! ভীষণ বিপদ।
অগত্যা বিধুশেখরকে রকেটে রেখেই আমরা তিনটি প্রাণী মঙ্গলগ্রহের মাটিতে পদাপর্ণ করলাম।
প্রথম পরিচয়ের অবাক ভাবটা দু’ঘণ্টার মধ্যে অনেকটা কেটে গেছে। নতুন জগতের যে একটা গন্ধ থাকতে পারে সেটা ভাবতে পারিনি। রকেট থেকে নেমেই সেটা টের পেলাম। এটা গাছপালা জলমাটির গন্ধ নয়–কারণ আলাদা করে প্রত্যেকটা জিনিস শুঁকে দেখেছি। এটা মঙ্গলগ্রহেরই গন্ধ, আবহাওয়ার সঙ্গে মিশে রয়েছে। হয়তো পৃথিবীর একটা গন্ধ রয়েছে যেটা আমরা টের পাই না, কিন্তু অন্য কোনও গ্রহের লোক সেখানে গেলেই পাবে।
প্রহ্লাদ পাথর কুড়িয়ে বেড়াচ্ছে। ওকে বলেছি কোনো প্রাণীটানি দেখলে আমায় খবর দিতে।
একদিকের আকাশে দেখছি সবুজ রঙে লালের ছোপ পড়েছে। এখন তা হলে বোধহয় ভোর, শিগগিরই সূর্য উঠবে।
মঙ্গল গ্রহের বিভীষিকা মন থেকে দূর হতে কত দিন লাগবে জানি না। কী করে যে প্রাণ নিয়ে বাঁচলাম সেটা ভাবতে এখনও অবাক লাগে। মঙ্গল যে কত অমঙ্গল হতে পারে, সেটা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি।
ঘটনাটা ঘটল প্রথম দিনেই।
সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আমি ঢিলার উপর থেকে উঠে জায়গাটা দিনের আলোয় একটু ভাল করে ঘুরে দেখবে ভাবছি। এমন সময় একটা আঁশটে গন্ধ আর একটা অদ্ভুত শব্দ শুনতে পেলাম। ঠিক মনে হল যেন একটা বেশ বড় রকমের ঝিঁঝি ‘তিন্তিড়ি তিন্তিড়ি’ বলে ডাকছে। আওয়াজটা কোন দিক থেকে আসছে সেটা বুঝবার চেষ্টা করছি এমন সময় একটা বিকট চিৎকারে আমার রক্ত জল হয়ে গেল।
তারপর দেখলাম প্রহ্লাদকে, তার চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসছে, ডান হাতের মুঠোয় নিউটনকে ধরে উর্ধ্বশ্বাসে এক-এক লাফে বিশ-পঁচিশ হাত করে রকেটের দিকে চলেছে।
তার পিছু নিয়েছে যে জিনিসটা সেটা মানুষও নয়, জন্তুও নয়, মাছও নয় কিন্তু তিনের সঙ্গেই কিছু কিছু মিল আছে। লম্বায় তিন হাতের বেশি নয়, পা আছে, কিন্তু তাহের বদলে মাছের মত ডানা, বিরাট মাথায় মুখজোড়া দন্তহীন হাঁ, ঠিক মাঝখানে প্রকাণ্ড একটা সবুজ চোখ আর সর্বাঙ্গে মাছের মতো আঁশ সকালের রোদে চিকচিক করছে।
জন্তুটা ভাল ছুঁটতে পারে না, পদে পদে হোঁচট খাচ্ছে। তাই হয়তো প্রহ্লাদের নাগাল পাবে না।
আমার যেটা সবচেয়ে সাংঘাতিক অস্ত্র সেটা হাতে নিয়ে আমি জন্তুটার পিছনে রকেটের দিকে ছুটলাম, প্রহ্লাদের যদি অনিষ্ট হয় তা হলেই অস্ত্রটা ব্যবহার করর, নয়তো প্রাণীহত্যা করব না।
আমি যখন জন্তুটার থেকে বিশ কি পঁচিশ গজ দূরে, তখনই প্রহ্লাদ রকেটে উঠে পড়েছে। কিন্তু এবারে আরেক কাণ্ড। বিধুশেখর এক লাফে রকেট থেকে নেমে জন্তুটাকে রুখে দাঁড়াল।
ব্যাপার দেখে আমিও থমকে দাঁড়ালাম। এমন সময় একটা দমকা হাওয়ার সঙ্গে আবার সেই আঁশটে গন্ধটা পেয়ে ঘুরেই দেখি ঠিক ওইটার মতো আরও অন্তত দু’-তিনশো জন্তু দূর থেকে দুলতে দুলতে রকেটের দিকে এগিয়ে আসছে। তাদের মুখ দিয়ে সেই বিকট ঝিঁঝির শব্দ–‘তিন্তিড়ি! তিন্তিড়ি! তিন্তিড়ি! তিন্তিড়ি! তিন্তিড়ি!–‘
বিধুশেখরের লোহার হাতের এক বাড়িতেই জন্তুটা ‘চী’ শব্দ করে ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে মাটিতে পড়ে গেল। পাছে ও রোখের মাথায় একাই এই মঙ্গলীয় সৈন্যকে আক্রমণ করে, তাই দৌড়ে গিয়ে বিধুশেখরকে জাপটে ধরলাম। কিন্তু ওর গোঁ সাংঘাতিক, আমায় সুদ্ধ হিঁচড়ে টেনে নিয়ে জন্তুগুলোর দিকে এগিয়ে চলল। আমি কোনও মতে কাঁধের কাছে হাতটা পৌঁছিয়ে বোতামটা টিপে দিলাম, বিধুশেখর অচল হয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। এ দিকে মঙ্গলীয় সৈন্য এখন একশো গজের মধ্যে। তাদের আঁশটে গন্ধে আমার মাথা ঘুরছে। ভৌতিক তিন্তিড়ি চিৎকারে কান ভোঁ ভোঁ করছে।
এখন এই পাঁচ-মনি যন্ত্রের মানুষটাকে রকেটে ওঠাই কী করে?
প্রহ্লাদকে ডেকে উত্তর পেলাম না।
কী বুদ্ধি হল, হাত দিয়ে বিধুশেখরের কোমরের কবজাটা খুজতে লাগলাম। বুঝতে পারছি মঙ্গলীয় সৈন্যের ঢেউ দুলতে দুলতে ক্রমশই এগিয়ে আসছে। আড়চোখে চেয়ে দেখি এখন প্রায় হাজার জন্তু, রোদ পড়ে তাদের আঁশের চকচকানিতে প্রায় চোখ ঝলসে যায়!
কোনওমতে বিধুশেখরকে দু’ভাগ করে ফেলে তার মাথার অংশটা টানতে টানতে রকেটের দরজার সামনে এনে ফেললাম। এবার পায়ের দিকটা। সৈন্য এখন পঞ্চাশ গজের মধ্যে। আমার হাত পা অবশ হয়ে আসছে। অস্ত্রের কথা ভুলে গিয়েছি।
পা ধরে টানতে টানতে বিধুশেখরের তলার অংশটা যখন রকেটের দরজায় এনে ফেললাম, তখন দেখি প্রহ্লাদের জ্ঞান হয়েছে। সে এরই মধ্যে ওপরের দিকটা ক্যাবিনের ভিতর তুলে দিয়েছে।
বাকি অংশটা ভিতরে তুলে ক্যাবিনের দরজা বন্ধ করার ঠিক আগ মুহূর্তে আমার পায়ে একটা ঠাণ্ডা স্যাঁতসেতে ঝাপটা অনুভব করলাম।
তারপর আর কিছুই মনে ছিল না।
যখন জ্ঞান হল দেখি রকেট উড়ে চলেছে। আমার ডান পায়ে একটা চিনচিনে যন্ত্রণা ও ক্যাবিনের মধ্যে একটা মেছো গন্ধ এখনও রয়ে গেছে।
কিন্তু রকেটটা উড়ল কী করে? চালাল কে? প্রহ্লাদ তো যন্ত্রপাতির কিছুই জানে না। আর বিধুশেখর তো এখনও দু’খান হয়ে পড়ে আছে। তবে কি আপনিই উড়ল নাকি? কিন্তু তাই যদি হয় তবে কোথায় চলেছে এই রকেট? কোথায় যাচ্ছি আমরা? সৌরজগতের অগণিত গ্রহনক্ষত্রের মধ্যে কোনটিতে গিয়ে আমাদের পাড়ি শেষ হবে? শেষ কি হবে, না অনির্দিষ্ট কাল আমাদের আকাশপথে অজানা উদ্দেশ্যে ঘুরে বেড়াতে হবে?
কিন্তু রসদ? সে ত অফুরন্ত নয়। আর তিন বছর পরে আমরা খাব কী?
রকেটের যন্ত্রপাতি নাড়াচাড়া করে দেখেছি তার কোনটাই কাজ করছে না। এই অবস্থায় রকেটের চলবারই কথা নয়। কিন্তু তাও আমরা চলেছি। কী করে চলেছি জানি না, কিছুই জানি না।
মনে অসংখ্য প্রশ্ন গিজগিজ করছে। কিন্তু কোনওটারই উত্তর দেবার শক্তি আমার নেই।
আজ থেকে আমি অজ্ঞান অসহায়।
ভবিষ্যত অজ্ঞেয়, অন্ধকার।
ব্যোমযাত্রীর ডায়রি – ০৪
এখনও আমরা একই ভাবে উড়ে চলছি।
কিছু দেখবার নেই, তাই জানালাটা বন্ধ করে রেখেছি।
প্রহ্লাদ এখন অনেকটা সামনে নিয়েছে। দাঁতকপাটি লাগাটাও কমেছে। নিউটনের অরুচিটাও কমেছে। মঙ্গলীয়ের গায়ে দাঁত বসানোর ফলেই বোধহয় ওটা হয়েছিল। কাণ্ডই বটে! প্রহ্লাদের কথাবার্তা এখনও অসংলগ্ন, কিন্তু যেটুকু বলেছে তার থেকে বুঝেছি যে নদীর ধারে পাথর কুড়োতে কুড়োতে সে হঠাৎ একটা আঁশটে গন্ধ পায়। তাতে সে মুখ তুলে দেখে কিছু দূরেই একটা না-মানুষ-না-জন্তু না-মাছ নদীর ধারে দাঁড়িয়ে আছে। আর নিউটন লেজ খাড়া করে চোখ বড় বড় করে গুটি গুটি সেটার দিকে এগোচ্ছে। প্রহ্লাদ কিছু করার আগেই নিউটন নাকি এক লাফে জন্তুটার কাছে গিয়ে তার হাঁটুতে এক কামড় দেয়। তাতে সেটা ঝিঁঝির মতো এক বিকট চিৎকার করে পালিয়ে যায়। কিন্তু তার পরমুহূর্তেই নাকি ঠিক ওই রকম আরেকটা জন্তু কোথা থেকে এসে প্রহ্লাদকে তাড়া করে। তার পরের ঘটনা অবিশ্যি আমার নিজের চোখেই দেখা।
বিধুশেখর আশ্চর্য সাহসের পরিচয় দিয়েছিল। তাই খুশি হয়ে এ-ক’দিন আমি ওকে বিশ্রাম দিয়েছি। আজ সকালে প্রহ্লাদ ও আমি ওকে জোড়া দিয়ে ওর কাঁধের বোতাম টিপে দিতেই ও স্পষ্ট উচ্চারণে বলল, ‘থ্যাঙ্ক ইউ’।
তারপর থেকেই ও আমার সঙ্গে বেশ পরিষ্কার ভাবে প্রায় মানুষের মতো কথা বলছে। কিন্তু কেন জানি না ও চলতি ভাষা না বলে শুদ্ধ ভাষা ব্যবহার করছে। বোধ হয় এত দিন প্রহ্লাদের মুখে রামায়ণ মহাভারত শোনার ফল।
আর সময়ের হিসেব নেই। সন-তারিখ সব গুলিয়ে গেছে। রসদ আর কয়েক দিনের মতো আছে। শরীর মন অবসন্ন। প্রহ্লাদ আর নিউটন নির্জীবের মতো পড়ে আছে। কেবল বিধুশেখরের কোনও গ্লানি নেই। ও বিড়বিড় করে সে কবে প্রহ্লাদের মুখে শোনা ঘটোৎকচবধের অংশটা আবৃত্তি করে যাচ্ছে।
আজও সেই ঝিমধরা ভাবটা নিয়ে বসেছিলাম এমন সময় বিধুশেখর হঠাৎ তার আবৃত্তি থামিয়ে বলে উঠল, ‘বাহবা, বাহবা, বাহবা’।
আমি বললাম, ‘কী হল বিধুশেখর, এত ফুর্তি কীসের?’
বিধুশেখর বলল, ‘গবাক্ষ উদ্ঘাটন করহ’।
এর আগে বিধুশেখরের কথা না শুনে ঠকেছি। তাই হাত বাড়িয়ে জানালাতা খুলে দিলাম। খুলতেই চোখঝলসানো দৃশ্য আমায় কিছুক্ষণের জন্য অন্ধ করে দিল। যখন দৃষ্টি ফিরে পেলাম, দেখি আমরা এক অদ্ভুত অবিশ্বাস্য জগতের মধ্য দিয়ে উড়ে চলেছি। যত দূর চোখ যায় আকাশময় কেবল বুদ্বুদ্ ফুটছে আর ফাটছে, ফুটছে আর ফাটছে। এই নেই এই আছে, এই আছে এই নেই।
অগুনতি সোনার বল আপনা থেকেই হঠাৎ বড় হতে হতে হঠাৎ ফেটে সোনার ফোয়ারা ছড়িয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে।
আমি যে অবাক হব তাতে আর আশ্চর্য কী? কিন্তু প্রহ্লাদ যে প্রহ্লাদ, সেও এই দৃশ্য দেখে মুগ্ধ না হয়ে পারেনি। আর নিউটন? সে ক্রমাগত ঝাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে জানালার কাচটা খামচাচ্ছে, পারলে যেন কাচ ভেদ করে বাইরে চলে যায়।
সে দিন থেকেয়ার জানালা বন্ধ করিনি। কারণ কখন যে কোন বিচিত্র জগতের মধ্যে এসে পড়ি তার ঠিক নেই। খিদেতেষ্টা ভুলে গেছি। ক্ষণে ক্ষণে দৃশ্য পরিবর্তন হচ্ছে। এখন দেখছি সারা আকাশময় সাপের মত কিলবিলে সব আলো এদিক ওদিক ছুটে বেড়াচ্ছে। এক একটা জানালার খুব কাছে এসে পড়ে, আর কেবিনের ভেতরটা আলো হয়ে ওঠে। এ যে সৌরজগতের কোনও বাদশাহের উৎসবে আতসবাজির খেলা।
আজকের অভিজ্ঞতা এক বিধুশেখর ছাড়া আমাদের সকলের ঘাম ছুটিয়ে দিয়েছিল। আকাশভর্তি বিশাল বিশাল গোলাকৃতি এবড়োথেবড়ো পাথরের চাঁই। তাদের গায়ের সব গহ্বরের ভিতর থেকে অগ্ন্যুদ্গার হচ্ছে। আমরা সেই পাথরের ফাঁক দিয়ে ফাঁক দিয়ে কলিশন বাঁচিয়ে বিদ্যুৎবেগে ছুটে চলেছি। প্রহ্লাদ ক্রমাগত ইষ্টনাম জপ করছে। নিউটন টেবিলের তলায় ঢুকে থরথর করে কাঁপছে। কতবার মনে হয়েছে এই বুঝি গেলাম, এই বুঝি গেলাম। কিন্তু রকেট ঠিক শেষ মুহূর্তে ম্যাজিকের মত মোড় ঘুরে নিজের পথ বেছে নিয়ে বেরিয়ে গেছে।
আমরা ভয়ে মরছি, কিন্তু বিধুশেখরের ভ্রুক্ষেপ নেই। সে তার চেয়ারে বসে দুলছে ও মধ্যে মধ্যে ‘টাফা’ বলছে।
এই একটা নতুন কথা কদিনই ওর মুখে শুনছি। বোধ হয় বাইরের দৃশ্য দেখে তারিফ করে ‘তোফা’ কথাটা বলতে গিয়ে টাফা বলছে। আজ নিউটনকে বড়ি খাওয়াচ্ছি, এমন সময় বিধুশেখর হঠাৎ এক লাফে জানালার কাছে গিয়ে ‘টাফা’ বলে চিৎকার করে উঠল। আমি জানালার দিকে তাকিয়ে দেখি–আকাশে আর কিছু নেই, কেবল একটা ঝলমনে সাদা গ্রহ নির্মল নিষ্কলঙ্ক একটি চাঁদের মতো আমাদের দিকে চেয়ে আছে।
রকেটটা নিঃসন্দেহে ওই গ্রহটার দিকেই এগিয়ে চলেছে। বিধুশেখরের কথা যদি সত্যি হয় তা হলে ওটার নাম টাফা।
ব্যোমযাত্রীর ডায়রি – ০৫
আজ জানালা দিয়ে অপূর্ব দৃশ্য। টাফার সর্বাঙ্গে যেন অসংখ্য জোনাকি জ্বলছে আর নিবছে। সেই আলোয় আমাদের কেবিনও আলো হয়ে গেছে। আমার সেই স্বপ্নের জোনাকির কথা মনে পড়েছে। মন আজ সকলেরই খুশি।
শেষ পর্যন্ত হয়তো আমাদের অভিযান ব্যর্থ হবে না।
টাফার দূরত্ব দেখে আন্দাজে মনে হচ্ছে কালই হয়তো আমরা ওখানে পৌঁছে যাব। গ্রহটা ঠিক কী রকম দেখতে সেটা ওই জোনাকিগুলোর জন্য বোঝবার উপায় নেই।
আজ বিধুশেখর যে সব কথাগুলো বলছিল সেগুলো বিশ্বাস করা কঠিন। আমি ক’দিন থেকে ওর অতিরিক্ত ফুর্তি দেখে বুঝেছি যে ওর ‘মাথা’টা হয়তো আবার গোলমাল করছে।
ও বলল টাফায় নাকি সৌরজগতের প্রথম সভ্য লোকেরা বাস করে। পৃথিবীর সভ্যতার চেয়ে ওদের সভ্যতা নাকি বেশ কয়েক কোটি বছরের পুরনো! ওদের প্রত্যেকটি লোকই নাকি বৈজ্ঞানিক এবং এত বুদ্ধিমান লোক একসঙ্গে হওয়াতে নাকি ওদের অনেক দিন থেকেই অসুবিধে হচ্ছে। তাই কয়েক বছর থেকেই নাকি ওরা অন্যান্য সব গ্রহ থেকে একটি কমবুদ্ধি লোক বেছে নিয়ে টাফায় আনিয়ে বসবাস করাচ্ছে।
আমি বললাম, ‘তা হলে ওদের প্রহ্লাদকে পেয়ে খুব সুবিধে হবে বলো।’ তাই শুনে বিধুশেখর ঠং ঠং করে হাততালি দিয়ে এমন বিশ্রীরকম অট্টহাসি আরম্ভ করল যে আমি বাধ্য হয়ে তার কাঁধের বোতামটা টিপে দিলাম।
কাল টাফায় এসে পৌঁছেছি। রকেট থেকে নেমে দেখি বহু লোক আমায় অভ্যর্থনা করতে এসেছে। লোক বলছি, কিন্তু এরা আসলে মোটেই মানুষের মতো নয়। অতিকায় পিঁপড়ে জাতীয় একটা কিছু কল্পনা করতে পারলে এদের চেহারার কিছুটা আন্দাজ পাওয়া যাবে। বিরাট মাথা, আর চোখ। কিন্তু সেই অনুপাতে হাত-পা সরু–যেন কোনও কাজেই লাগে না। এদের সম্বন্ধে বিধুশেখর যা বলছিল তা যে একদম ভুল সে বিষয়ে কোনও সন্দেহই নেই। আমার বিশ্বাস ব্যাপারটা আসলে ঠিক তার উলটো। অর্থাৎ এরা মানুষের অবস্থা থেকে এখনও অনেক পিছিয়ে আছে, এবং সে অবস্থায় পৌঁছতে ঢের সময় লাগবে।
টাফার অবস্থা যে পৃথিবীর তুলনায় কত আদিম তা এতেই বেশ বোঝা যায় যে এদের ঘরবাড়ি বলে কিছু নেই–এমনকী গাছপালাও নেই। এরা গর্ত দিয়ে মাটির ভিতর ঢুকে যায় এবং সেখানেই বাস করে। অবিশ্যি এরা ঠিক আমার দেশের বাড়ির মতো একটা বাড়ি দিয়েছে। কেবল ল্যাবরেটরিটাই নেই, আর সবই যেমন ছিল ঠিক তেমনি।
প্রহ্লাদ ও নিউটন দিব্যি আছে। নতুন গ্রহে এসে নতুন পরিবেশে যে বাস করছে সে বোধটাই যেন নেই।
বিধুশেখরকেই কেবল দেখতে পাচ্ছি না, ও কাল থেকেই উধাও। টাফা সম্পর্কে এতগুলো মিথ্যা কথা বলে হয়তো আর মুখ দেখানোর সাহস নেই।
আজ থেকে ডায়েরি লেখা বন্ধ করব–কারণ এখানে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটার কোনও সম্ভাবনা দেখছি না। খাতাটা পৃথিবীতে ফেরত পাঠানোর কোনও উপায় নেই এটা খুব আক্ষেপের বিষয়। এত মূল্যবান তথ্য রয়েছে এতে! এখানকার মূর্খরা তো মর্ম কিছুই বুঝবে না–আর এ দিকে আমাকেও ফিরে যেতে দেবে না।
ফিরে যাওয়ার খুব যে একটা প্রয়োজন বোধ করছি তাও নয়–কারণ এরা সত্যি আমায় খুব যত্নে রেখেছে। বোধ হয় ভাবছে যে আমার কাছ থেকে অনেক কিছু আদায় করে নেবে।
এরা বাংলাটা জানল কী করে জানি না–তবে তাতে একটা সুবিধে হয়েছে যে ধমক টমক দিলে বোঝে। সে দিন একটা পিঁপড়েতে ডেকে বললাম, ‘কই হে, তোমাদের বৈজ্ঞানিক-টৈজ্ঞানিকরা সব কোথায়? তাদের সঙ্গে একটু কথাটথা বলতে দাও। তোমরা যে ভয়ানক পিছিয়ে আছ।’
তাতে লোকটা বলল, ‘ও সব বিজ্ঞানটিজ্ঞান দিয়ে আর কী হবে? যেমন আছেন থাকুন না। আমরা মাঝে মাঝে আপনার কাছে আসব। আপনার সহজ সরল কথাবার্তা শুনতে আমাদের ভারী ভাল লাগে।’
আহা! যত সব ন্যাকামো।
আমি রেগে গিয়ে আমার নস্যির বন্দুকটা নিয়ে লোকটার ঠিক নাকের ফুটোয় তাক করে মারলাম।
কিন্তু তাতে ওর কিছু হল না।
হবে কী করে? এরা যে এখনও হাঁচতেই শেখেনি!
[অনেকে হয়তো জানতে চাইবে প্রোফেসর শঙ্কুর ডায়রিটা কোথায় এবং এমন আশ্চর্য জিনিসটাকে দেখবার কোনও উপায় আছে কি না। আমার নিজের ইচ্ছে ছিল যে, ডায়েরিটা ছাপানোর পর ওর কাগজ ও কালিটা বৈজ্ঞানিককে দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে তারপর ওটাকে জাদুঘরে দিয়ে দেব। সেখানে থাকলে অবিশ্যি সকলের পক্ষেই দেখা সম্ভব। কিন্তু তা হবার জো নেই। না থাকার কারণটা আশ্চর্য। লেখাটা কপি প্রেসে দেবার পর সেই দিনই বাড়ি এসে শোবার ঘরের তাক থেকে ডায়রিটা নামাতে গিয়ে দেখি জায়গাটা ফাঁকা। তারপর একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখলাম। ডায়েরির পাতার কিছু গুঁড়ো আর লাল মলাটটার ছোট্ট একটা অংশ তাকের উপর আছে। এবং তার উপর ক্ষিপ্রপদে ঘোরাফেরা করছে প্রায় শ-খানেক বুভুক্ষু ডেঁয়োপিঁপড়ে। এরা পুরো খাতাটাকে খেয়ে শেষ করেছে, এবং ওই সামান্য বাকি অংশটুকু আমার চোখের সামনেই উদরসাৎ করে ফেলল। আমি কেবল হাঁ করে চেয়ে রইলাম।
যে জিনিসটাকে অক্ষয় অবিনশ্বর বলে মনে হয়েছিল, হঠাৎ পিঁপড়ের খাদ্যে পরিণত হল কী করে সেটা আমি এখনও ভেবে ঠাহর করতে পারিনি। তোমরা এর মানে কিছু বুঝতে পারছ কি?]