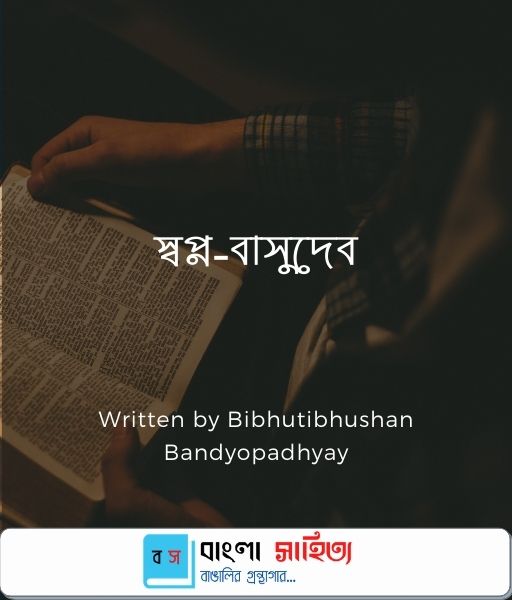বাড়ি বসিয়া লিখিতেছিলাম। সকালবেলাটায় কে আসিয়া ডাকিল— জ্যাঠামশাই?.একমনে লিখিতেছিলাম, একটু বিরক্ত হইয়া বলিলাম—কে?
বালিকা-কণ্ঠে কে বলিল—এই আমি, হাজু।
—হাজু? কে হাজু?
বাহিরে আসিলাম। একটি ষোলো-সতরো বছরের মলিন বস্ত্র পরনে মেয়ে একটি ছোটো ছেলে কোলে দাঁড়াইয়া আছে। চিনিলাম না। গ্রামে অনেকদিন পরে নতুন আসিয়াছি, কত লোককে চিনি না। বলিলাম—কে তুমি?
মেয়েটি লাজুক সুরে বলিল—আমার বাবার নাম রামচরণ বোষ্টম।
এইবার চিনিলাম-রামচরণের সঙ্গে ছেলেবেলায় কড়ি খেলিতাম। সে আজ বছর পাঁচ-ছয় হইল ইহলোকের মায়া কাটাইয়া সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করিয়াছে সে সংবাদও রাখি। কিন্তু তাহার সাংসারিক কোনো খবর রাখিতাম না। তাহার যে এতবড়ো মেয়ে আছে, তাহা এখনই জানিলাম।
বলিলাম—ও! তুমি রামচরণের মেয়ে? বিয়ে হয়েছে দেখচি, শ্বশুরবাড়ি কোথায়?
–কালোপুর।
–বেশ বেশ। এটি খোকা বুঝি? বয়েস কত হল?
—এই দু-বছর।
—বেশ। বেঁচে থাকো। যাও বাড়ির মধ্যে যাও।
—আপনার কাছে এইচি জ্যাঠামশাই, আপনি লোক রাখবেন?
—লোক? না, তোক তো আছে গয়লা-বউ। আর লোকের দরকার নেই তো। কেন? থাকবে কে?
—আমি থাকতাম। আপনার মাইনে লাগবে না, আমাদের দুটো খেতে দেবেন।
—কেন, তোমার শ্বশুরবাড়ি?
মেয়েটি কোনো জবাব দিল না। অতশত হাঙ্গামাতে আমার দরকার কী? লেখার দেরি হইয়া যাইতেছে, সোজাসুজি বলিলাম—না, লোকের এখন দরকার নেই আমার।
তারপর মেয়েটি বাড়ির মধ্যে ঢুকিল এবং পরে শুনিলাম সে ভিক্ষা করিতে আসিয়াছিল। চাল লইয়া চলিয়া গিয়াছে।
মেয়েটির কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম, হঠাৎ একদিন দেখি, রায়েদের বাহিরের ঘরের পৈঠায় বসিয়া সেই মেয়েটি হাউহাউ করিয়া একটুকরা তরমুজ খাইতেছে। যেভাবে সে তরমুজের টুকরাটি ধরিয়া কামড় মারিতেছে, ‘হাউহাউ’ কথাটি সুষ্ঠুভাবে সেক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং ওই কথাটাই আমার মনে আসিল। অতিমলিন বস্ত্র পরিধানে। ছেলেটি ওর সঙ্গে নাই। পাশে পৈঠার উপরে দু-এক টুকরা পেঁপে ও একখণ্ড তালের গুড়ের পাটালি। অনুমানে বুঝিলাম আজ অক্ষয় তৃতীয়া উপলক্ষ্যে রায়-বাড়ি কলসী-উৎসর্গ ছিল, এসব ফলমূল ভিক্ষা করিতে গিয়া প্রাপ্ত। কারণ মেয়েটির পায়ের কাছে একটা পোঁটলা এবং সম্ভবত তাহাতে ভিক্ষায় পাওয়া চাল।
সেদিন আমি কাহাকে যেন মেয়েটির সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলাম। শুনিলাম মেয়েটি শ্বশুরবাড়ি যায় না, কারণ সেখানকার অবস্থা খুবই খারাপ, দু-বেলা ভাত জোটে না। চালাইতে না-পারিয়া মেয়েটির স্বামী উহাকে বাপেরবাড়ি ফেলিয়া রাখিয়াছে, লইয়া যাবার নামও করে না। এদিকে বাপেরবাড়ির অবস্থাও অতিখারাপ। রামচরণ বোষ্টমের বিধবা স্ত্রী লোকের বাড়ি ঝি-বৃত্তি করিয়া দুটি অপোগণ্ড ছেলে-মেয়েকে অতিকষ্টে লালনপালন করে। মেয়েটি মায়ের ঘাড়ে পড়িয়া আছে আজ একবছর। মা কোথা হইতে চালাইবে, কাজেই মেয়েটিকে নিজের পথ নিজেই দেখিতে হয়।
একদিন আমাদের বাড়ির ঝি গয়লা-বউকে কথায় কথায় জিজ্ঞেস করাতে সে বলিল—হাজু নাকি আপনার বাড়ি থাকবে বলেছিল?
—হ্যাঁ। বলেছিল একদিন বটে।
–খবরদার বাবু, ওকে বাড়িতে জায়গা দেবেন না, ও চোর।
—চোর? কীরকম চোর?
—যা সামনে পাবে তাই চুরি করবে। মুখুজ্যেবাড়ি রাখেনি ওকে, যা-তা চুরি করে খায়, দুধ চুরি করে খায়, চাল চুরি করে নিয়ে যায়—আর বড্ড খাই-খাই— কেবল খাব আর খাব। ওর হাতির খোরাক জোগাতে না-পেরে মুখুজ্যেরা ছাড়িয়ে দিয়েছে। এখন পথে পথে বেড়ায়।
—ওর মা ওকে দেখে না?
—সে নিজে পায় না পেট চালাতি! ওকে বলেছে, আমি কনে পাব? তুই নিজেরটা নিজে করে খা। তাই ও দোরে দোরে ঘোরে।
সেই হইতে মেয়েটির ওপর আমার দয়া হইল। যখনই বাড়ি আসিত, চাল বা ডাল, দু-চারিটা পয়সা দিতাম। বার দুই দুপুরে ভাত খাইয়া গিয়াছে আমার বাড়ি হইতে।
মাসখানেক পরে একদিন আমার বাড়ির সামনে হাউমাউ কান্না শুনিয়া বাহিরে গেলাম। দেখি হাজু কাঁদিতে কাঁদিতে আমাদের বাড়ির দিকে আসিতেছে। ব্যাপার কী? শুনিলাম মধু চক্রবর্তী নাকি তাহার আর কিছু রাখে নাই, তাহার হাতে একটা ঘটি ছিল, সেটিও কাড়িয়া রাখিয়া দিয়াছে—তাহাদের বাড়িতে ভিক্ষা করিতে গিয়াছিল, এই অপরাধে।
রাগ হইল। আমি গ্রামের একজন মাতবর, এবং পল্লিমঙ্গল সমিতির সেক্রেটারি, তখনই মধু চক্রবর্তীকে ডাকিয়া পাঠাইলাম। মধু একখানা রাঙা গামছা কাঁধে হন্তদন্ত হইয়া আমার বাড়ি হাজির হইল। জিজ্ঞাসা করিলাম—মধু, তুমি একে মেরেচ?
—হ্যাঁ দাদা, এক ঘা মেরেছি ঠিকই। রাগ সামলাতে পারিনি, ও আস্ত চোর একটি। শুনুন আগে, আমাদের বাড়ি ভিক্ষে করতে গিয়েছে, গিয়ে উঠোনের লঙ্কা গাছ থেকে কোঁচড়ভরে কাঁচা-পাকা লঙ্কা চুরি করেছে প্রায় পোয়াটাক। আর একদিন অমনি ভিক্ষে করতে এসে, দেখি বাইরের উঠোনের গাছ থেকে একটা পাকা পেঁপে ভাঙচে, সেদিন কিছু বলিনি—আজ আর রাগ সামলাতে পারিনি দাদা। মেরেচি এক চড়, আপনার কাছে মিথ্যে বলব না।
—না, খুবই অন্যায় করেচ। মেয়েমানুষের গায়ে হাত তোলা, ওসব কী? ইতরের মতো কাণ্ড। ছিঃ—যাও, ওর কী নিয়ে রেখেচ ফেরত দাও গে যাও।
হাজুকেও বলিয়া দিলাম, সে যেন আর কোনোদিন মধু চক্রবর্তীর বাড়ি ভিক্ষা করিতে না-যায়।
এই সময় আকাল শুরু হইয়া গেল। ধান-চাল বাজারে মেলে না, ভিখিরিকে মুষ্টিভিক্ষা দেওয়া বন্ধ। এই সময় একদিন হাজুকে দেখিলাম ছেলে কোলে গোয়ালপাড়ার রাস্তায় ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছে। আমাকে দেখিয়া নির্বোধের মতো চাহিয়া বলিল—এই যে জ্যাঠামশায়।…যেন মস্ত একটা সুসংবাদ দিতে অনেকক্ষণ হইতেই আমাকে খুঁজিতেছে।
আমি একটু বিরক্তির সহিত বলিলাম—কী?
—এই! আপনাদের বাড়িও যাব।
—বেশ। আমাদের বাড়িতে প্রসাদ পাবি আজ–বুঝলি?
হাজু খুব খুশি। খাইতে পাইলে মেয়েটা খুব খুশি হয় জানি। কাঁটালতলার ছায়ায় রোয়াকে সে যখন খাইতে বসিল, তখন দুজনের ভাত তাহার একার পাতে। নিছক খাওয়ার মধ্যে যে কী আনন্দ থাকিতে পারে তাহা জানিতে হইলে হাজুর সেদিনকার খাওয়া দেখিতে হয়। স্ত্রীকে বলিয়া দিলাম—একটু মাছ-টাছ বেশি করে দিয়ে ওকে খাওয়াও…।
একদিন বোষ্টমপাড়ার হরিদাস বৈরাগীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমাদের পাড়ার হাজু শ্বশুরবাড়ি যায় না কেন?
—ওকে নেয় না ওর স্বামী।
—কারণ?
—সে নানান কথা। ও নাকি মস্ত পেটুক, চুরি করে হাঁড়ি থেকে খায়। দুধের সর বসবার জো নেই কড়ায়, সব চুরি করে খাবে। তাই তাড়িয়ে দিয়েছে।
-এই শুধু দোষ? আর কিছু না?
—এই তো শুনিচি, আর তো কিছু শুনিনি। তারাও ভালো গেরস্ত না। তাহলে কী আর ঘরের বউকে তাড়িয়ে দেয় খাওয়ার জন্যে? তারাও তেমনি।
কিছুদিন আর হাজুকে রাস্তাঘাটে দেখা যায় না। একদিন তাদের পাড়ার বোষ্টমবউ বলিল—শুনেছেন কাণ্ড?
—কী?
—সেই হাজু আমাদের পাড়ার, সে যে বনগাঁয়ে গিয়ে নাম লিখিয়েছে।
আমি দুঃখিত হইলাম। এদেশে নাম লেখানো বলে বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করাকে। হাজু অবশেষে পতিতাবৃত্তি গ্রহণ করিল। খুব আশ্চর্যের বিষয় নয় এমন কিছু, তবু দুঃখ হয় গ্রামের মেয়ে বলিয়া। এখানেই এ ব্যাপারের শেষ হইয়া যাইত হয়তো, কারণ গ্রামে সবসময়ে থাকিও না, থাকিলেও সকলের খবর সবসময় কানেও আসে না।
পঞ্চাশের মন্বন্তর চলিয়া গেল। পথের পাশে এখানে-ওখানে আজও দু-একটা কঙ্কাল দেখা যায়। ত্রিপুরা জেলা হইতে আগত বুভুক্ষু নিঃস্ব হতভাগ্যেরা পৃথিবীর বুকে চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। এ জেলায় মন্বন্তরের মূর্তি অত তীব্র ছিল না। যে দেশে ছিল, সে দেশ হইতে নিঃস্ব নরনারী এখানে আসিয়াছিল, আর ফিরিয়া যায় নাই।
পৌঁষ মাসের দিন। খুব শীত পড়িয়াছে। মহকুমার শহরে একটা পাঠাগারের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে গিয়াছি, ফিরিবার পথে একটা গলির মধ্যে দিয়া বাজারে আসিয়া উঠিব ভাবিয়া গলির মধ্যে ঢুকিয়া কয়েক পদ মাত্র অগ্রসর হইয়াছি, এমন সময় কে ডাকিল—ও জ্যাঠামশায়।
বলিলাম—কে?
—এই যে আমি।
আধ-অন্ধকার গলিপথে ভালো করিয়া চাহিয়া দেখিবার চেষ্টা করিলাম। একটা চালাঘরের সামনে পথের ধারে একটি মেয়ে রঙিন কাপড় পরিয়া দাঁড়াইয়া আছে, কাপড়ের রঙ অন্ধকারের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে, আমি শুধু তাহার মুখের আবছায়া আদল ও হাত দুটি দেখিতে পাইলাম।
কাছে গিয়ে বলিলাম—কে?
—বা রে, চিনতে পারলেন না? আমি হাজু।
হাজু বলিলেও আমার মনে পড়িল না কিছু। বলিলাম—কে হাজু?
সে হাসিয়া বলিল—আপনাদের গাঁয়ের। বা রে, ভুলে গেলেন? আমার বাবার নাম রামচরণ বৈরাগী। আমি যে এই শহরে নটী হয়ে আছি।
এমন সুরে সে শেষের কথাটি বলিল, যেন জীবনের পরমসার্থকতা লাভ করিয়াছে এবং সেজন্য সে গর্ব অনুভব করে। অর্থাৎ এত বড়ো শহরে নটী হইবার সৌভাগ্য কী কম কথা, না যার-তার ভাগ্যে তা ঘটে? গ্রামের লোক, দেখিয়া বুঝুক তার কৃতিত্বের বহরখানা।
আমি কিছু বলিবার পূর্বেই সে বলিল—আসুন না দয়া করে আমার ঘরে।
—না, এখন যেতে পারব না। সময় নেই।
—কেন, কী করবেন?
—বাড়ি যাব।
সে আবদারের সুরে বলিল—না, আসতেই হবে। পায়ের ধুলো দিতেই হবে আমার ঘরে। আসুন—
কি ভাবিয়া তাহার সঙ্গে ঢুকিয়া পড়িলাম তাহার ঘরে। নীচু রোয়াকে খড় ছাওয়া, রোয়াক পার হইয়া মাঝারি ধরনের একটি ঘর, ঘরে একখানা নীচু তক্তপোশের উপর সাজানো-গোছানো ফর্সা চাদরপাতা বিছানা। দেয়ালে বিলিতি সিগারেটের বিজ্ঞাপনের ছবি দু-তিনখানা। মেমসাহেব অমুক সিগারেট টানিতেছে। একখানা ছোটো জলচৌকির উপর খানকতক পিতল-কাঁসার বাসন রেড়ির তেলের প্রদীপের অল্প আলোয় ঝকঝক করিতেছে। মেঝেতে একটা পুরোনো মাদুর পাতা। বোষ্টমের মেয়ে, একখানা কেষ্টঠাকুরের ছবিও দেয়ালে টাঙানো দেখিলাম। ঘরের এক কোণে ডুগিতবলা একজোড়া, একটা হুঁকো, টিকে তামাকের মালসা, আরও কী কী।
হাজু গর্বের স্বরে বলিল—এই দেখুন আমার ঘর—
—বাঃ, বেশ ঘর তো! কত ভাড়া দিতে হয়?
—সাড়ে সাত টাকা।
—বেশ। হাজু একঘটি জল লইয়া আসিয়া বলিল—পা ধুয়ে নিন—
—কেন? পা ধোয়া এখন কোনো দরকার দেখচি নে, আমি এক্ষুনি চলে যাব।–একটু জল খেয়ে যেতে হবে কিন্তু এখানে জ্যাঠামশায়।
এখানে জলযোগ করিবার প্রবৃত্তি হয় কখনো? পতিতার ঘরদোর। গা ঘিন ঘিন করিয়া উঠিল। বলিলাম—না, এখন কিছু খাব না। সময় নেই—
হাজু সে কথা গায়ে না-মাখিয়া বলিল—তা হবে না। সে আমি শুনচিনে— কিছুতেই শুনব না—বসুন—
তাহার পর সে উঠিয়া জলচৌকি হইতে চায়ের পেয়ালা তুলিয়া আনিয়া সযত্নে সেটা আঁচল দিয়া মুছিয়া আমাকে দেখাইয়া বলিল—দেখুন, কিনিচি—আপনাকে চা করে খাওয়াব এতে—চা করতে শিখিচি।
ড্রেসডেন চায়না নয়, অন্য কিছু নয়, সামান্য একটা পেয়ালা। হাজুর মনস্তুষ্টির জন্য বলিলাম—বেশ জিনিস, বাঃ—
ও উৎসাহ পাইয়া আমাকে ঘরের এজিনিস-ওজিনিস দেখাইতে আরম্ভ করিল। একখানা আয়না, একটা টুকনি ঘটি, একটা সুদৃশ্য কৌটা ইত্যাদি। এটা কেমন? ওটা কেমন? সে এসব কিনিয়াছে। তাহার খুশি ও আনন্দ দেখিয়া অতিতুচ্ছ জিনিসেরও প্রশংসা না-করিয়া পারিলাম না। এতক্ষণ ভাবিতেছিলাম, ইহাকে এ পথে আসিবার জন্য তিরস্কার করি এবং কিছু সদুপদেশ দিয়া জ্যাঠামশায়ের কর্তব্য সমাপ্ত করি। কিন্তু হাজুর খুশি দেখিয়া ওসব মুখে আসিল না।
যে কখনো ভোগ করে নাই, তাহাকে ত্যাগ করো যে বলে, সে পরমহিতৈষী সাধু হইতে পারে, কিন্তু সে জ্ঞানী নয়। কাল ও ছিল ভিখারিনি, আজ এ পথে আসিয়া ওর অন্নবস্ত্রের সমস্যা ঘুচিয়াছে, কাল যে পরের বাড়ি চাইতে গিয়া প্রহার খাইয়াছিল, আজ সে নিজের ঘরে বসিয়া গ্রামের লোককে চা খাওয়াইতেছে, নিজের পয়সায় কেনা পেয়ালা-পিরিচে—যার বাবাও কোনোদিন শহরে বাস করে নাই বা পেয়ালায় চা পান করে নাই। ওর জীবনের এই পরমসাফল্য ওর চোখে। তাহাকে তুচ্ছ করিয়া, ছোটো করিয়া, নিন্দা করিবার ভাষা আমার জোগাইল না।
সংকল্প ঠিক রাখা গেল না। হাজু চা করিয়া আনিল। আর একখানা কাঁসার মাজা রেকাবিতে স্থানীয় ভালো সন্দেশ ও পেঁপে কাটা। কত আগ্রহের সহিত সে আমার সামনে জলখাবারের রেকাবি রাখিল।
সত্যিই আমার গা ঘিন ঘিন করিতেছিল।
এমন জায়গায় বসিয়া কখনো খাই নাই—এমন বাড়িতে।
কিন্তু হাজুর আগ্রহভরা সরল মুখের দিকে চাহিয়া পাত্রে কিছু অবশিষ্ট রাখিলাম। হাজু খুব খুশি হইয়াছে—তাহার মুখের ভাবে বুঝিলাম।
বলিল—কেমন চা করিচি জ্যাঠামশায়? চা মোটেই ভালো হয় নাই—পাড়াগেঁয়ে চা, না-গন্ধ, না-আস্বাদ। বলিলাম— কোথাকার চা?
—এই বাজারের।
—তুই নিজে চা খাস?
—হুঁ, দুটি বেলা। চা না-খেলে সকালে কোনো কাজ করতে পারিনে, জ্যাঠামশায়।
আমার হাসি পাইল। সেই হাজু!–
ছবিটি যেন চোখের সামনে আবার ফুটিয়া উঠিল। রায়বাড়ির বাহিরের ঘরের পৈঠার কাছে বসিয়া খোলাসুদ্ধ তরমুজের টুকরা হাউহাউ করিয়া চিবাইতেছে। সেই হাজু চা না-খাইলে নাকি কোনো কাজে হাত দিতে পারে না।
বলিলাম—তা হলে এখন উঠি হাজু। সন্দে উতরে গেল। আবার অনেকখানি রাস্তা যাব।
হাজুর দেখিলাম, এত শীঘ্র আমাকে যাইতে দিতে অনিচ্ছা। গ্রামের এ কেমন আছে, সে কেমন আছে, জিজ্ঞাসাবাদ করিল। বলিল—একটা কথা জ্যাঠামশায়, মাকে পাঁচটা টাকা দেব, আপনি নিয়ে যাবেন? লুকিয়ে দিতে হবে কিন্তু টাকাটা। পাড়ার লোকে না-জানতে পারে। মার বড়ো কষ্ট। আমি মাসে মাসে যা পারি মাকে দিই। গত মাসে একখানা কাপড় পাঠিয়েছিলাম।
কার হাতে দিয়ে দিলি?
—বিনোদ গোয়ালা এসেছিল, তার হাত দিয়ে লুকিয়ে পাঠালাম।
—তোর ছেলেটা কোথায়?
—মার কাছেই আছে। ভাবচি এখানে নিয়ে আসব। সেখানে খেতে-পরতে পাচ্ছে না। এখানে খাওয়ার ভাবনা নেই জ্যাঠামশায়, দোকানের খাবার খেয়ে তো অছো হল। সিঙ্গেড়া বলুন, কচুরি বলুন, নিমকি বলুন—তা খুব। এমন আলুর দম করে ওই বটতলার খোট্টা দোকানদার, অমন আলুর দম কখনো খাইনি। এই এত বড়ো বড়ো এক-একটা আলু—আর কত রকমের মশলা—আপনি আর একটু বসবেন? আমি গিয়ে আলুর দম আনব, খেয়ে দেখবেন!
নাঃ, ইহার সরলতা দেখিয়াও হাসি পায়। রাগ হয় না ইহার উপর। বলিলাম— না, আমি এখন যাচ্ছি। আর ওই টাকাটা আমি নিয়ে যাব না, তুমি মনিঅর্ডার করে পাঠালেও তো পারো। অন্য লোকে দেবে কি না দেবে—বিনোদ যে তোমার মাকে টাকা দিয়েছে, তার ঠিক কী?
হাজুর এ সন্দেহ মনে উঠে নাই এতদিন। বলিল—যা বলেচেন জ্যাঠামশাই, টাকাটা জিনিসটা তো এর-ওর হাতে দিয়ে পাঠিয়ে দিই, মা পায় কিনা পায় তা কী
জানি!
—এ পর্যন্ত কত টাকা দিয়ে?
—তা কুড়ি-পঁচিশ টাকার বেশি। আমি কী হিসেব জানি জ্যাঠামশাই? মা কষ্ট পায়, আমার তা কী ভালো লাগে?
—কার হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিস?
হাজু সলজ্জ মুখে চুপ করিয়া রহিল। বুঝিলাম আমাদের গ্রামের লোকজন ইহার নিকট যাতায়াত করে।
বলিলাম—আচ্ছা দে সেই পাঁচটা টাকা।—চলি—
—আবার আসবেন জ্যাঠামশাই। বিদেশে থাকি, মাঝে মাঝে দেখেশুনে যাবেন এসে।
গ্রামে ফিরিয়া হাজুর মায়ের সঙ্গে দেখা করিয়া টাকা পাঁচটি তাহার হাতে দিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম—আর কেউ তোমাকে কোনো টাকা দিয়েছিল?
হাজুর মা আশ্চর্য হইয়া বলিল—কই না! কে দেবে টাকা?
বিনোদ ঘোষের নাম করিতে পারিতাম। কিন্তু করিলে কথাটা জানাজানি হইয়া পড়িবে। বিনোদ ভাবিবে আমারও ওখানে যাতায়াত আছে এবং হাজুর প্রণয়ীদে