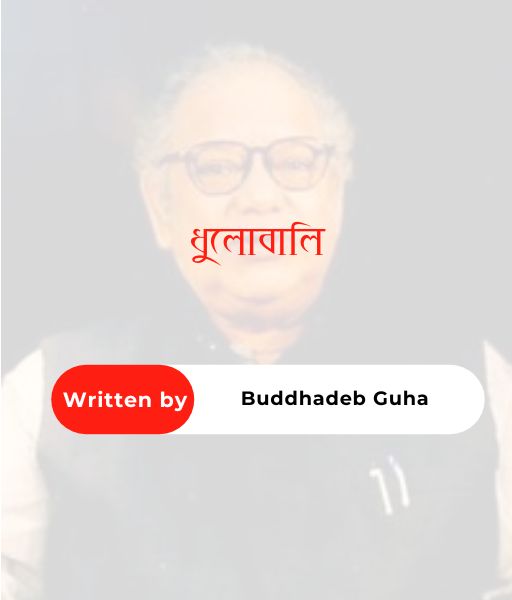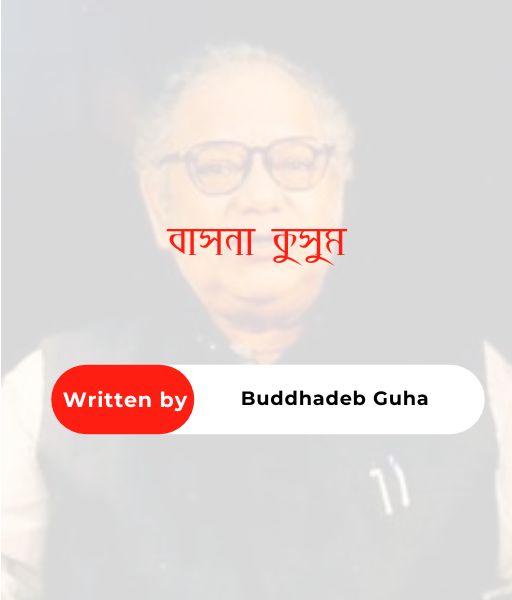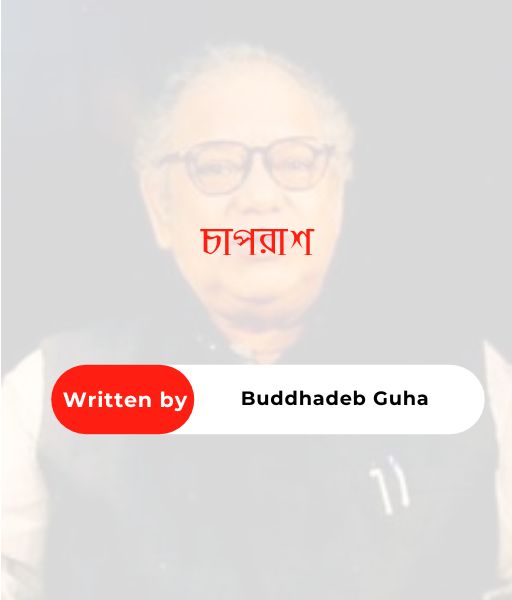দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর
০৫.
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর অষ্ট্রিয়ার ন্যাটো কি সেন্টো কোনো জোটেই যোগ দেওয়ার উপায় নেই। তাহলে ভার্সাইলস-এর চুক্তি অনুযায়ী রাশিয়া সঙ্গে সঙ্গে আক্রমণ করে বসতে পারে অস্ট্রিয়াকে।
ইনসত্ৰুক জায়গাটা চমৎকার। ইন নদীর উপত্যাকায় এই ইনসব্রুক। ইন নদীর সঙ্গে ইছামতীর তুলনা করা চলে–যদিও চওড়ায় অনেক কম এই নিটোল টলটলে নদী। নদীর ওপর কাঠের সাঁকো। রাজহাঁস চরে বেড়াচ্ছে। অস্ট্রেলিয়ান রাজহাঁসও আছে। শুনবিলড হাঁসও দেখলাম কয়েকটা।
ইনসব্রুকের হাঁক-ডাক আছে শপিংসেন্টার হিসাবে। কিন্তু আমাদের মতো গরিব দেশের গরিব লোকেদের এসব জায়গায় দাম ও নাম দেখেই নিরস্ত থাকতে হয়। কোনো কিছু ভালো জিনিস কেনার সামর্থ্য আমাদের নেই বললেই চলে। দোকানের শো-কেসে যেসব স্কিইং ইকুইপমেন্টস দেখলাম, মুখে মুখে তার দাম যোগ করে প্রায় সাত আট হাজার টাকা দাঁড়াল। আমাদের পক্ষে ভাবাই মুশকিল। তবে ওই জিনিসই আমরা ওর চেয়ে অনেক সস্তায় তৈরি করতে পারতাম।
ইনসব্রুক-এর গ্র্যাণ্ড থিয়েটারের সামনের চত্বরে এসে বাস দাঁড়াল। এখান থেকে অন্য ট্যুর যাবে। যারা বেশি পয়সা দিয়ে এই অন্য ট্যুরের টিকিট কেটেছেন সারাদিনের, তাঁরা এতে যাবেন। যারা কাটেননি আমার মতো, তাঁদের সারাদিন ফ্যা ফ্যা করে ইনসকের পথে-পথে ঘুরে বেড়াতে হবে।
এখন ছুটির সময়। আজ বারটাও রোববার। চারদিকে ওপেন-এয়ার রেস্তোরাঁ, কাফে। কিছু জায়গায় আর্টিস্টরা বসে গেছে লাইন দিয়ে পোর্ট্রেট আঁকবার জন্যে। কড়ি ফেলো; আর ছবি আঁকাও। তবে বেশির ভাগ ছবিই এমন হচ্ছে যে, একেবারে ফাস্টোকেলাশ। ওই ছবি দেখে উত্তমর্ণর পক্ষে অধমর্ণকে চেনা প্রায় অসম্ভব। এটা একটা কম-অ্যাডভানটেজ নয়।
কিছুক্ষণ পর আমাদের টা-টা করে যাঁরা নতুন ট্যুরে যাবার তাঁরা চলে গেলেন। আমরা কয়েকজন পড়ে রইলাম ইতস্তত। কমবয়েসি নীল চোখের অস্ট্রেলিয়ান মেয়ে কোরাল (ক্যারল নয়), তার বয়ফ্রেণ্ড–পাকা পাকা চেহারার মুখময় বণ ওঠা ছোঁড়া, কয়েকজন বুড়ো ও বেতো দম্পতি এবং আমি।
গ্র্যাণ্ড থিয়েটারে মোজার্ট-এর কনসার্ট হচ্ছিল। চত্বরে ফোয়ারা। পায়রারা ওড়াউড়ি করছিল। ঝকঝকে রোদ। কলকাতার গড়ের মাঠে যেমন শীতের দুপুরে রাজ্যের বেকার ভবঘুরে শুয়ে বসে রোদ পোয়ায়, বা কানের ময়লা পরিষ্কার করায়, বা জয় বজরঙ্গবলী কা জয় বলে চেঁচামেচি করে কুস্তি লড়ে, না হয় কুস্তি দেখে; এখানেও তেমন রগড় করা এবং রগড় দেখার লোকের অভাব নেই দেখলাম।
সব দেশেই লম্বা লোক, বেঁটে লোক, কাজের লোক, কুঁড়ে লোক, ভালো লোক, খারাপ লোক থাকে।
গ্র্যাণ্ড থিয়েটারের উলটো দিকেই রাজপ্রাসাদ। এই প্রাসাদ নেপোলিয়ন দখল করে ফেলেছিলেন। ইতিহাসের অনেক সাক্ষ্য বহন করছে এই প্রাসাদ। ইনসব্রুকের মিউজিয়ামও বিখ্যাত। মিউজিয়ামে নেপোলিয়নের ইনসব্রুক আক্রমণের একটা দুর্দান্ত সার্কুলার ফ্রেসকো আছে। দেখবার মতো।
সাইটসিয়িং ট্যুরের বাস চলে যাওয়ার পর কিছুক্ষণ হাঁটহাঁটি করে একটা ওপেন-এয়ার কাফেতে একক্যান বিয়ার নিয়ে বসে চিঠি লিখতে বসলাম।
কলকাতার সাঙ্গুভ্যালি রেস্তোরাঁতে ডাবল-হাফ চা নিয়ে নির্লজ্জতার পরাকাষ্ঠা করে যতক্ষণ বসে থাকা সম্ভব তার চেয়েও নির্লজ্জ হয়ে একক্যান বিয়ার নিয়ে বসে ঘণ্টা দুই কাটালাম। পকেটে যা পয়সা ছিল তা দিয়ে একটা ক্রিস্টাল নেকলেস কিনেছিলাম দেশে যাকে ভালোবাসি তেমন একজনের জন্যে। সেটা কিনে ফেলার পর খুচরো পয়সাও রইল না যে কিছু খাই। সমস্তটা দিন পড়ে আছে সামনে–গ্র্যাণ্ড থিয়েটারের সামনে বাস আসবে সেই শেষবিকেলে। এদিকে এমন ঠাণ্ডা দিন-দুপুরেও যে, এক জায়গায় বসে থাকলে কষ্ট হয়। কিন্তু হাঁটাও বা কাঁহাতক যায়?
দেশে থাকতে টানাটানি গেছে, অবস্থার উত্থান-পতন হয়েছে কিন্তু কখনো এমন অবস্থা হয়নি যে, পকেটে এককাপ কফি খাওয়ার মতোও পয়সা নেই। পকেটে পয়সা না থাকাটা যে কত অসহায়, করুণাকর ও হীনমন্য অনুভূতি তা সেই দিন ইনসকে হাড়ে হাড়ে বুঝেছিলাম। সেটা একটা খুব বড়ো শিক্ষা সন্দেহ নেই।
যাঁরা সাইট-সিয়িং ট্যুরে গেছিলেন তাঁরা কখন যে সব দেখে-টেখে ফিরে আসবেন, তা তাঁরাই জানেন।
এদিকে সারাদিন শূন্য-পকেটে হি-হি ঠাণ্ডায় হেঁটে হেঁটে ও উইণ্ডো শপিং করে রীতিমতো ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। যে স্কোয়ারে আমরা বাস থেকে নেমেছিলাম সেই স্কোয়ারে এসে তখন অনেকেই জমায়েত হয়েছেন।
বেলা পড়ে এসেছে। পশ্চিমাকাশের রোদ এসে ভরে দিয়েছে জায়গাটা। লানডানের ট্রাফালগার স্কোয়ারের মতো একটা ঝরনা। তার পাশে ওখানকার মতোই অনেক পায়রা ওড়াউড়ি করছে। ভ্যাগাবণ্ড, ট্যুরিস্ট, ভবঘুরে, কুঁড়ে; নানারকমের লোকের ভিড়। কেউ চকোলেট খাচ্ছে রোদে বসে, কেউ বা আইসক্রীম; কোনো বৃদ্ধ পাশে লাঠি রেখে বেঞ্চে বসে বিকেলের খবরের কাগজ পড়ছেন।
স্কোয়ারের সামনেই এ্যাণ্ড থিয়েটার। আগেই বলেছিলাম যে মোজার্ট-এর কনসার্ট হচ্ছে সেখানে। কিন্তু কনডাকটেড ট্যুরের হতভাগ্য লোকেদের তো কোনো স্বাধীনতা নেই যে, ইচ্ছামতো কোথাও তারা থামে। পায়ে দড়ি বাঁধা তাদের সকলের, গাইডের হাতের ঘড়ির সঙ্গে।
কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে না করতেই আমাদের বাস এসে হাজির হল। আমরা উঠে পড়লাম।
যাঁরা ভাগ্যবান, দিনভর অনেক কিছু দেখে এলেন, কিনে এলেন। তাঁরা অনেকের প্রশ্নের উত্তরে উত্তেজিত হয়ে তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা বলতে লাগলেন।
জ্যাক বাস ছেড়ে দিল, অ্যালাস্টার আমাদের মাল-জান বুঝে নেবার পর।
হোটেলে ফিরে তাড়াতাড়ি মুখ-হাত ধুয়ে নিয়ে ডিনার সেরে নেওয়ার পর আবার আমরা হোটেল টীরল-এ এলাম! অস্ট্রিয়ার মনোরম পরিবেশে এমন সুন্দর হোটেলটা, যে কী বলব।
সেই হোটেলেই অস্ট্রিয়ানদের ফোক-লোর দেখার ও শোনার জন্যে রাতে গেছিলাম সকলে। সঙ্গে স্ন্যাপস ও অস্ট্রিয়ান রেড ওয়াইন বা হোয়াইট ওয়াইন যে যা খেল তাই পরিবেশিত হল। মস্ত বড় কাঠের ফ্লোরের তিনপাশে বসার জায়গা করা হয়েছিল ডাইনিং রুমে। ছেলেরা চামড়ার শর্টস পরে আর সাদা জামার ওপর লাল-রঙা ওয়েস্ট-কোটের মতো কোট পরে উরুতে, নিতম্বে জুতোর তলায়, গালে ফটাফট চটাচট তালি দিয়ে দিয়ে নাচল। মেয়েরা ঘুরে ঘুরে। কাঠুরেদের নাচ দেখাল একটা। সঙ্গে গান। সঙ্গত হিসেবে গরুর গলার ঘণ্টা আর অ্যাকর্ডিয়ান।
ওদের নাচ দেখতে দেখতে দর্শকদের মধ্যেও অনেকে স্ন্যাপস ও ওয়াইন খেয়ে চেগে উঠে নাচতে লাগলেন। সেই ব্রাসেলসে পাসপোর্ট হারিয়ে-যাওয়া মহিলা মিস ফাস্ট এমন সাজে সেজে এসেছিলেন যে সকলেরই চোখে পড়ছিলেন তিনি। তাঁর মাথার চুল রুপোলি, বয়েস পঞ্চাশের ওপরে, কিন্তু অনেকগুলো ওয়াইন গেলার পর তাঁর চোখ-মুখের ভাব পালটে গেল। অথচ ছেলে-ছোকরাদের মধ্যে কেউ তাঁকে নাচার জন্য নেমন্তন্ন করল না। বুড়োরা নিজের স্ত্রী ছাড়া, অন্য কমবয়েসি মেয়েদের সঙ্গে নাচতে চাইছিল। কিন্তু ওঁর সঙ্গে নয়।
এমন সময়, সমস্ত ফ্লোরের সবচেয়ে হ্যাণ্ডসাম, বছর চল্লিশের বয়সের এক অস্ট্রিয়ান অথবা জার্মান ভদ্রলোক উঠে এসে ওঁর সামনে বাও করে বললেন, মে আই?
সঙ্গে সঙ্গে সেখানে যত সুন্দরী মেয়েরা ছিল তাদের সকলের মুখ শুকিয়ে গেল। কিন্তু তখনও তো আমাদের মহিলা নাচ শুরুই করেননি।
মহিলার আজ গোলাপি পোশাক, হাতে গোলাপি পাখা পুরোনো দিনের ব্যারনেসদের মতো ছোটোবেলায় ইংরিজি সিনেমাতে আমরা বল-নাচের দৃশ্যে যেমন পোশাক ও পাখা দেখতাম, তেমন।
কিন্তু নাচ শুরু হতেই সকলের চোখ কপালে উঠে গেল। কী সুন্দর ছন্দজ্ঞান, বাজনার সঙ্গে সঙ্গে সে কী অপূর্ব নাচ! কে বলবে যে তাঁর বয়েস পঞ্চাশের ওপর হয়েছে? নাচতে নাচতে উনি যেন কোনো গোলাপি পাখি হয়ে গেলেন। আমরা সকলে হতবাক। এই ঝগড়াটি ঝগড়াটি চেহারার চুপচাপ মহিলা আমদের কসমস ট্যুর নাম্বার টু-টুয়েন্টি-ট্যুর প্রত্যেকের বুকের ছাতি গর্বে ফুলিয়ে দেবেন তা আধ ঘণ্টা আগে অনুমানও করতে পারিনি।
জ্যাক দু-হাত জড়ো করে হাততালি দিয়ে বলল, গুড, গুড। নো-প্রবলেম।
কিন্তু নো-প্রবলেম কথাটা জ্যাক ঠিক বলেনি। ভদ্রমহিলার ততক্ষণে নেশা হয়ে গেছিল। আর তাঁর নাচের নমুনা দেখে সেখানের সমস্ত পুরুষ একবার করে তাঁর সঙ্গে নেচে নিজেদের ধন্য করতে চাইছিলেন। আমাদের সঙ্গের বুড়িরা বড়ো বড়ো হাই তুলছিলেন। এবং স্বামীদের দিকে বিরক্তির চোখে চাইছিলেন। বুড়োরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো মহিলার দিকে চেয়েছিলেন। তাতে বুড়িরা আরও চটে গিয়ে অ্যালাস্টারকে তাড়া লাগাচ্ছিলেন হোটেলে ফেরার জন্যে।
কিন্তু ফিরতে চাইলেই বা ফিরছে কে? ততক্ষণে নরক গুলজার। শেষে তিন-চারজন মিলে ভদ্রমহিলাকে প্রায় পাঁজাকোলা করে তুলে এনে বাসে পোঁছোনো হল।
বেশিমাত্রায় মদ খেয়ে ফেলেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর নাচ দেখে মনে হল বয়েসকালে তিনি একজন কেউ-কেটা ছিলেন।
বাস ছাড়তেই বাসের বর্ষীয়সী মহিলারা ওই মহিলাকে নিয়ে এমন টিকাটিপ্পনী কাটতে লাগলেন যে আমার মনে হল ওদের সমাজও শরৎবাবুর পল্লিসমাজের চেয়ে এখনও খুব একটা বেশি এগোয়নি। অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানতে ও মানতে হল যে, পৃথিবীর বর্ষীয়সী মহিলাকুলে কোনো তারতম্য নেই। ঈর্ষা, পরচর্চা, ফিসফিসানি সব হুবহু এক। শুধু এঁদের পোশাক বিভিন্ন, গায়ের রং, চেহারা ও ভাষা বিভিন্ন।
জ্যাক ভদ্রমহিলাকে বাসে তোলার সময়ে তাঁর হাতের পাতায় চুমু খেয়ে আবারও বলেছিল, গুড গুড, নো-প্রবলেম।
সেরাতে, রাত-শেষে উঠে বাথরুমে গেছিলাম। বাথরুম থেকে ফেরার সময়ে দেখি চোরের মতো পা-টিপে জ্যাক সেই মহিলার ঘরের দরজা বাইরে থেকে বন্ধ করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে। আমাকে দেখেই জ্যাক প্রথমে চমকে উঠল। তারপর হাসল কর্ণমূল বিস্তার করে। তারপরই বলল, নো-গুড।
মাই-ডিউটি।
জ্যাকের ইংরিজি ভাষার মর্ম উদ্ধার করার চেষ্টা তখনকার মতো না করে গিয়ে শুয়ে পড়লাম। পরে অনেকদিন জ্যাকের ওই কথা দুটোর মানে ভেবেছি। যতবার ভেবেছি ততবারই নতুন নতুন মানে পেয়েছি।
সত্যিই! জ্যাক আমাদের রিয়্যাল গ্রেট। ভার্সেটাইল জিনিয়াস।
ইটালির প্রোগ্রাম তো গতরাতেই ক্যানসেল হয়েছিল। আজ ভোরে তবুও আলবার্গ পাস পেরিয়েই আমাদের সুইটজারল্যাণ্ডে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু পুলিশের কাছে খবর নিয়ে জানা গেল যে, আলবার্গ পাসও এখনও আমাদের পেরুবার উপযুক্ত হয়নি।
আজ সকালে অস্ট্রেলিয়ান মেয়ে দুটি–যারা ব্রাসেলসের সকালে ঘুম থেকে উঠতে দেরি করেছিল, সেই ক্যারল আর জেনি আমাদের সঙ্গে যাবে। আমাদের বাস ছাড়ার আগে ভোগসওয়াগেন গাড়িটাতে করে (যাতে ওরা ওদের ছেলে-বন্ধুদের সঙ্গে কয়েক দিন-রাত কাটিয়েছে) ছেলেদুটি রওয়ানা হয়ে গেল ম্যুনিখে। ক্যারল যখন বাসে এসে উঠল, তখন পরিষ্কার দেখলাম ওর চোখের কোণে জল টলটল করছে। জেনি অন্যরকম। ও চোখ-মেরে ওর বয়ফ্রেণ্ডকে বিদায় জানাল।
আলবার্গ পাসে না যেতে পেরে আমরা কার্ন পাস পেরিয়ে এলাম আবার জার্মানিতে ঢুকে। কান পাসটি বড়ো সুন্দর। আল্পস-এর পাইন বন, ফার বন বরফ আর বরফ। দু-দিকে কী গাঢ় সবুজ সব গড়ানো উপত্যকা–ছবির মতো ঘরবাড়ি–ঘন নীল-রঙা জলের ফার্ন লেক। মাথা উঁচু পাহাড়ের নীচে। জঙ্গলের ছায়া পড়েছে জলে। মন বলে ওঠে কী সুন্দর; কী সুন্দর।
জার্মানি থেকে আমরা লিচেকটাইনে এসে ঢুকলাম। এই ছোট্ট রাজ্যটিতে এখনও ফিউডাল প্রথা আছে। অস্ট্রিয়ার রাজাদের কাছ থেকে কাউন্ট অফ লিচেকটাইন বাষট্টি বর্গমাইল জায়গা কিনে নিয়েছিলেন। এখনও এই রাজ্য কাউন্ট চালান। কাউন্টের রাজবাড়ি দেখলাম, পাহাড়ের ওপর চার-শো ফিট উঁচুতে।
আবারও ভাবছিলাম এরকম একটা ছোটোখাটো রাজ্য,ছিমছাম ছোটোখাটো রাজবাড়ি, ছিপছিপে একজন রানি থাকলে এ-জীবনে মন্দ হত না, ভাবনাটা গাঢ় হতে না হতেই শহর ছাড়িয়ে এলাম আমরা।
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে লিচেকটাইন অস্ট্রিয়া থেকে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে এখন সুইটজারল্যাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে।
লিচেকটাইন শহর পেরুবার পরই আমরা রাইন নদী পেরিয়ে সুইটজারল্যাণ্ডে এসে ঢুকে পড়লাম। সামনেই লেক লুজার্ন। লুজার্ন-লেকের দৃশ্যের তুলনা হয় না। সুইটজারল্যাণ্ডকে কেন পৃথিবীর সবচাইতে সুন্দর জায়গা বলে তা এখানে না এলে বোঝা যাবে না।
পথটা চলে গেছে লেকের বাঁ-পাশ দিয়ে। ওপাশে বরফাবৃত মাথা-উঁচু পাহাড়-আল্পস শ্রেণি। পথটা ক্রমাগত একটার পর একটা টানেলের মধ্যে দিয়ে চলেছে। আবার কখনো বা লেক লুজার্নের গা-ঘেঁষে, নীল আকাশের নীচে-নীচে।
যখন লেক লুজার্ন পেরিয়ে এসে লুজার্নে পৌঁছোলাম তখন সন্ধে হয়ে গেছে। লুজার্ন লেকের ওপর নানারঙা আলোর প্রতিফলন। দূরে জলের ওপরে একটা মেলা-মতন বসেছে। সেখান থেকে রঙিন আলোর ছটা আর ট্যাঙ্গো নাচের বাজনা ভেসে আসছে।
লেক লুজার্নের পাশের এই গ্রামটির নাম ফ্লুইলেন। হোটেলের নাম, হোটেল ক্রুজ।
সারাপথেই, জার্মানি ও অস্ট্রিয়াতে বিশেষ করে অস্ট্রিয়ার স্কিয়িং-এর এলাকাগুলোতে দেখেছি যে, এখানে ওখানে লেখা আছে গাস্টফ এবং জিমার। অর্থাৎ গেস্টহাউস, ঘর পাওয়া যায়। যারা স্কিইং করতে হুট-হাট চলে আসে উইক-এণ্ডে এবং হোটেলে জায়গা পায় না অথবা হোটেলে থাকার যাদের সামর্থ্য নেই; তারা এমনি সব ঘরে থেকে যায়। স্থানীয় লোকদের ভালো উপরি রোজগার হয় এই সময়ে–এক-আধটা বাড়তি ঘর থাকলেই হল। বেশির ভাগই বেড অ্যাণ্ড ব্রেকফাস্ট।
আগেই বলেছি যে, কন্টিনেন্টের ব্রেকফাস্ট আমাদের দেশের প্রাচীনপন্থী বিধবাদের রাতের খাওয়ার মতো শর্টকাটের। এখনও পশ্চিমে শুধু ইংল্যাণ্ড ও কন্টিনেন্টেই বেড এবং ব্রেকফাস্ট প্রথা চালু আছে হোটেলগুলোতে। নইলে অন্যত্র, এমনকী ভারতবর্ষের সমস্ত ফাইভস্টার হোটেলেই এখন আমেরিকান প্ল্যান চালু। অর্থাৎ বেড ওনলি। যদি কেউ কিছু খান, সে বেড টি খেলেও তা একস্ট্রা।
একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। সকালবেলা আজ বেরুনোর পরই সরু পাহাড়ি রাস্তার পর একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল। রাস্তাঘাট দার্জিলিংয়ের মতো। কিন্তু অত্যন্ত শার্প সব বাঁক। প্রত্যেক বাঁকের মুখে বিরাট বিরাট আয়না লাগানো, যাতে বাঁক নেবার আগে অন্য গাড়ির ছায়া তাতে ভেসে ওঠে।
এমনি এক বাঁক পেরুতেই আমাদের বাসটা একটা সাদা মার্সিডিস গাড়ির মুখোমুখি এসে পড়ল। লেটেষ্ট মডেলের ডিজেল মার্সিডিস। গাড়িটার সাদা রং, হলুদ ফগ লাইট, মাথায় লাল সিল্কের স্কার্ফ জড়ানো মহিলা আরোহী মিলেমিশে দারুণ দেখাচ্ছিল। বেশ জোরেই আসছিল গাড়িটা–আমাদের বাসের সঙ্গে ধাক্কা লাগল। মুখোমুখি নয়, পাশাপাশি।
গাড়িটা জোরে এলেও জ্যাক একেবারে কপিবুক ড্রাইভারের মতো সাবধানে বাঁকটা নিয়েছিল আস্তে–কিন্তু তাতেও স্পর্শ এড়ানো গেল না। মুহূর্তের মধ্যেই দুটো গাড়িই থেমে গেল। গাড়ির আরোহীদের মধ্যে একজন এসে সাদা চক দিয়ে পথের ওপরে বাস ও গাড়ির চাকার পাশে দাগ দিয়ে দিলেন। পথের দোকান থেকে ফোন করল জ্যাক। তিন-চার মিনিটের মধ্যে দুজন পুলিশ দুটি গাড়ি নিয়ে এসে হাজির। তারা নেমে নোটবইয়ে কীসব লিখলেন দাগ দেখে। বাস ও গাড়ির ড্রাইভারের লাইসেন্স ও ইনশিওরেন্সের কার্ড দেখলেন। তারপর দুজনের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করে চলে গেলেন। গাড়ি ও বাস যে যার পথে চলল। সুন্দর গাড়িটার একটা হেডলাইট চুরমার হয়ে গেছিল।
ব্যাপারটা আমার মনঃপুত হল না। ভিড় জমল না, চেঁচামেচি হল না। মার শালাকে, ধর শালাকে হল না! সেলফ অ্যাপয়েন্টেড ভলান্টিয়াররা এল না, মাতব্বরি করল না–অর্থাৎ অ্যাক্সিডেন্টের মতো একটা জমজমাট কান্ড ঘটা সত্ত্বেও কোনো পথচারীর একটুও ঔৎসুক্য জাগল না। থার্ড ক্লাস।
রাতের খাওয়া-দাওয়ার পর লেক লুজার্নের পাশে হেঁটে এলাম কিছুটা। রাতেরবেলা কী যে সুন্দর দেখাচ্ছিল লেকটাকে।
পরদিন ভোরে উঠে ব্রেকফাস্ট সেরে ফ্লুইলেন থেকে লুজার্নে এলাম আবার। মাইল তিরিশের পথ। আসলে এখানে হোটেল অনেক সস্তা লুজার্নের থেকে। তাই এই গরিব গুরববাদের এতদূরে নিয়ে এসে রাত কাটানোর ব্যবস্থা।
লুজার্ন লেকে বোটে চড়ে আমরা চললাম আল্পনাকষ্টাড-এ। বোট মানে ডিঙি নৌকো নয়। একেবারে আধুনিক সেন্ট্রালি হিটেড চতুর্দিকে কাঁচ বসানো রেস্তোরাঁ-সম্পন্ন মোটরবোট। বোটের মধ্যে ঢুকে প্রাণ বাঁচল। বাইরে আজ বড়ো ঠাণ্ডা। হাড়-কাঁপানো হাওয়া দিচ্ছে। রোদে দাঁড়িয়েও অবস্থা কাহিল। সেপ্টেম্বরের শেষ–সুইটজারল্যাণ্ড বলে ব্যাপার। জানি না। ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে এখানে কী হি-হি অবস্থা হয়?
ছোটোবেলা থেকে মাউন্টেন রেলওয়ের কথা শুনেছি; ছবি দেখেছি। এই মাউন্টেন রেলওয়ে দার্জিলিং ও সিমলার মতো নয়। পাহাড়ের গা দিয়ে একেবারে সটান সোজা উঠে গেছে। ঘুরে ঘুরে কু-ঝিকঝিক করে যাওয়ার কোনো ব্যাপারই নেই।
আমরা যাব মাউন্ট পিলাটাস-এ। চারহাজার ফিট উঁচু। এ আমাদের দেশ নয়। আল্পস-এ বিশেষ করে সুইস আল্পস-এ এ-সময় দু-হাজার ফিটেই বরফ থাকে। মাউন্ট পিলাটাসকে জার্মান ভাষায় বলে পিলাটাসকুলম।
পঁয়তাল্লিশ থেকে আটচল্লিশ ডিগ্রি সোজা ট্রেনটা উঠে চলল। বসার সিটগুলোও এমনভাবে তৈরি যে যাত্রীরা গড়িয়ে যাতে না পড়ে যান তেমন বন্দোবস্ত আছে। দুটো স্টেজে কোচ চেঞ্জ করতে হয়–চালু অনুযায়ী বন্দোবস্ত।
দেখতে দেখতে মিনিট পনেরো-কুড়ির মধ্যে একেবারে পাহাড়ের চুড়োয় এসে হাজির হলাম। মাঝামাঝি থেকেই বরফ পড়ছিল। চুড়োয় তো একেবারে সাদা। কোচ থেকে বাইরে বেরিয়ে যা শীত তা বলার নয়। তবে সেখানেও হিটেড রেস্তোরাঁ আছে। সেখানে কিছুক্ষণ বসে কফি খেয়ে গা গরম করে কেবল-কার-এ করে আমরা নেমে এলাম আবার যেখান থেকে এসেছিলাম তার পাশেই।
পুরো সুইটজারল্যাণ্ডে কতরকম প্রক্রিয়ায় যে ট্যুরিস্টদের পয়সা খরচ করানো যায় তার সমস্ত পথই এরা বের করে রেখেছে। মাউন্ট পিলাটাস থেকে ফিরতে ফিরতে বেলা হল। আমাদের রাঁদেভু পয়েন্টে ফিরে গিয়ে অনেকে আবার বিকেলে আর একটা বোটট্রিপ নিল। কিন্তু আমার আর্থিক অবস্থার জন্যে কতকটা এবং কিছুটা সারাদিন একগাদা লোকের সঙ্গে হই হই করতে ভালো লাগে না বলে আমি গেলাম না।
ভেবেছিলাম একা একা লুজার্নের পথে হেঁটে বেড়াব। একা একা হাঁটার মতো সুখ বুঝি আর বেশি নেই। কত কী ভাবা যায় মনে মনে, নিরুচ্চারে নিজের সঙ্গে, অন্যের সঙ্গে, কত কী কথা কওয়া যায়।
কিন্তু বিধি বাম!
সবে পায়ারে দাঁড়িয়ে, বোটে ওঠা বাসের সহযাত্রীদের হাত নেড়ে বিদায় জানিয়েছি। আর পেছন থেকে এসে জ্যাক বলল, মিস্টার! লোনলি?
আমি বললাম, না না বাবা, সবসময়ে হই-হুঁল্লোড় আমার ভালো লাগে না। এ-কদিনেই তবিয়ৎ খারাপ হয়ে গেছে। এখন একটু একা থাকতে ইচ্ছা হয়েছে।
শুনে জ্যাক তো চোখ কপালে তুলল।
ওর মুখের অভিব্যক্তি দেখে মনে হল যে হয় ও আমায় থানায় দেবে নইলে হাসপাতালে ভরতি করবে।
একা থাকার কথাতেই ও বোধহয় নির্ঘাৎ আমার শারীরিক বা মানসিক কোনো অসুখ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়ে উঠেছে। আসলে ওর দোষও নেই।
যাদের নিয়ে ওর বরাবর আসতে হয় সেইসব বুকে তিনটে করে ক্যামেরা ঝোলানো সারাদিন লম্ফঝম্ফ করে বেড়ানো হনুমানসুলভ যূথবদ্ধ মানুষগুলোর মধ্যে কারও কারও যে এমন রোগ থাকতে পারে এ জ্যাকের মতো সাদাসিধে মানুষের ধারণার বাইরে। হনুমান হলে দোষ ছিল না। ও ভ্যারাণ্ডার ফুল অথবা কোনো চিরঞ্জীব বনৌষধির মূল খেয়ে নিতে বলতে পারত।
কিন্তু হনুমান নই বলে ও আমাকে নিয়ে যে কী করবে ভেবে পেল না।
আমি ওকে যে বোঝাব তেমন উপায়ও ছিল না। জ্যাক ইংরিজি খুব কম জানে। তবু ও হয়তো আমার মুখ দেখে বুঝে থাকবে যে এই রোগীর সিমটম এ-ধরনের অন্য রোগীর মতো নয়। তাই আমার হাত ধরে প্রায় টানতে টানতেই নিয়ে গিয়ে একটা কাফেতে ঢোকাল। এবং নিজে পয়সা দিয়ে আমাকে কফি খাওয়াল।
তারপর চোখ মেরে বলল, বাইরে বড়ো ঠাণ্ডা। চলো সিনেমা দেখি।
আমি প্রতিবাদ করে উঠলাম। অপছন্দের সিনেমা দেখার মতো ক্রিমিনাল ওয়েস্ট অফ টাইমে আমি অবিশ্বাসী। কিন্তু কে কার কথা শোনে।
কাউন্টারে নিয়ে গিয়ে জ্যাকই টিকিট কাটতে চাইল। কিন্তু ভারতবর্ষের ইজ্জত রাখতে আমাকেই টিকিটের দামটা দিতে হল।
ছবিটা না দেখলেই পারতাম। উল ব্রেনার নায়ক। কিন্তু তাঁকে এমন এক গল্পে এবং এমন এক চরিত্রে অভিনয় করতে দেখলাম–এক রোবোটের ভূমিকায়–যে, তাঁর দ্বারা এতাবৎ অর্জিত এবং ম্যাগনিফিসেন্ট সেভেন-এর সময় থেকে জমিয়ে-রাখা তাঁর প্রতি আমার সমস্ত প্রশংসা সেদিন লুজার্ন লেকের ঠাণ্ডা জলে ধুয়ে দিয়ে এলাম।
সিনেমা যখন ভাঙল তখন সন্ধে হবো হবো। বোট-ট্রিপ ফিরে এল একটু পর। তারপর লেকের পাশ থেকেই সকলে একসঙ্গে বাসে উঠে ফিরে এলাম ফ্লুইলেনে রাতের মতো।
আজ সারা হোটেলেই ছিল। বলল ওর জ্বর। আমি বলেছিলাম যে আমি থাকি ওকে দেখাশোনা করার জন্যে। তাতে ও হেসেছিল। বলেছিল ইজরায়েলের মেয়েরা এত সহজেই পরনির্ভর হয় না। তারপর আমার হাতে আলতো করে চড় মেরে বলেছিল, জানো এ ক-দিন আমার ভাবনাগুলো সব যেন বাসের ডিফারেনসিয়ালের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে গুঁড়িয়ে গেল। একটু স্থিতি দরকার। গো অ্যাহেড. তুমি যাও। তুমি এদেশে শিগগিরি আবার নাও আসতে পারো। আমি আমার এক বন্ধুর সঙ্গে সামনের বছর আবার আসব। ডোন্ট মিস দ্য ফান।
ফান আবার কী?
বেলুন ওড়ানো বাবল-গাম চিবুনোর বয়েসের পর পুজোয় নতুন জুতো নতুন জামা পরার আনন্দের পর ফান বলে আর কিছুই থাকে না আমাদের জীবনে। ওদের হয়তো আছে। আমাদের এখানে তারপর থোর-বড়ি-খাড়া খাড়া-বড়ি-থোর। বেশির ভাগেরই। তার কারণ হয়তো আনন্দ করা, পরকে আনন্দ দেওয়া ও নির্ভেজাল আনন্দে আনন্দিত হওয়ার ক্ষমতা আমরা অনেকেই বড়ো তাড়াতাড়ি হারিয়ে ফেলি।
হোটেলে ফিরেই সারার ঘরে গেলাম। ওর ঘরের দরজায় টোকা দিতেই একটু পর দরজা খুললেন রয়্যাল এয়ার ফোর্সের সাহেব।
কিন্তু দরজা পুরো খুললেন না। আড়াল থেকে মুখটা বার করলেন শুধু। বললেন, শি ইজ সিক। আই অ্যাম ডকটরিং হার। ইটস আ উইণ্ডফল।
আমি অবাক হয়ে এবং কিঞ্চিৎ উদবেগের সঙ্গে বললাম, হাউ ইজ শি?
পাইলট দরজার আড়াল থেকে উইংক করলেন।
বললেন, ওঃ ডোন্ট ওয়ারি! শি ইজ গুড। বাট আই অ্যাম টেকিং হার আ প্রসেস অফ গুড-বেটার-বেসট।
ভেতর থেকে সারার খিলখিল হাসি শুনতে পেলাম।
আমি চলে যাবার আগেই আর. এ. এফ-এর সাহেব আমার নাম ধরে ডেকে বললেন, আই লাইক ইণ্ডিয়ান্স। উই হ্যাভ বিন টুগেদার ইন দ্য ওয়ার। লেট আস বি টুগেদার ইন পিস।..এণ্ড ইন লাভ।
বলেই বললেন, ডোন্ট ডিসকাস দিস ম্যানলি অ্যাফেয়ার উইথ আ উম্যান আই মিন, মাই ওয়াইফ।
আমি আরও অবাক হয়ে বললাম, হোয়্যার ইজ শি?
ওঃ, শি হ্যাজ গান টু সী আ ব্যাচেলার ফ্রেণ্ড অফ হার। এন ওল্ড টাইমার।
তারপর একটু থেমে বলল, ঊ্য নো, ইটস আ কাইণ্ড অফ ফ্লাটেশান–ইটস কাটিং বোথ অফ আস। ইকুয়ালি ওয়েল।
ভেতর থেকে সারা কী যেন একটা দুম করে ছুঁড়ে মারল। আধখোলা দরজার সামনে ঝুপ করে পড়ল সেটা।-বালিশ।
সারা বলল, কাম ব্যাক কুইক ঊ্য ড্যাম ফুল সিলি ব্যাবলিং ইংলিশম্যান।
সাহেব বলল, ডোন্ট বি ইমপেশেন্ট! উ্য আনগ্রেটফুল বার্ডি! উই হ্যাভ প্লেন্টি অফ টাইম টু স্পিল।
আমি আমার ঘরের দিকে এগিয়ে গেলাম।
উষ্ণতা-ফুষ্ণতা সব তাহলে বোগাস। হৃদয়-কৃদয়, ভালোলাগা বলে তবে কি সারার কিছুই নেই? ও কি সোনালি নীম্ফ?
.
০৬.
ডিনার টেবলে আজ ক্যারল আর জেনির সঙ্গে মুখোমুখি বসা হয়েছিল। আসলে কে কোথায় বসবেন তা ঠিক থাকে না। কখনোই। কিছু কিছু লোক সব জায়গাতেই নিজেদের দল নিয়ে খেতে বসেন। এও একরকমের ক্ল্যানিশ মেন্টালিটি। অন্যেরা বেশির ভাগই যেদিন যাদের টেবলে জায়গা হয় বসে যান।
সেদিন সারার ঘরে গিয়ে ও তারপর নিজের ঘরে গিয়ে হাতমুখ ধুতে দেরি হয়ে গেছিল। যখন ডাইনিং রুমে এলাম তখন ওদের টেবলেই শুধু জায়গা খালি ছিল। ওদের সঙ্গে এর আগে ফর্মালি আলাপ হয়নি। আলাপ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ওরা আমার ফারস্ট নেম শুধোল। এটাই আজকালকার ফ্যাশান। মিস্টার সেন বা মিস্টার জোসেফ বা মিস হল্যাণ্ড বলে কেউ কাউকে ডাকে না আজকাল। আজকাল সত্যিকারের অন্তরঙ্গতা বোধহয় কারও সঙ্গেই কারও হয় না বলেই লোকে প্রথম আলাপেই অন্যকে অন্তরঙ্গ ভাবতে চায়-পদবি ধরে না ডেকে প্রথম নাম এমনকী ডাকনামেও ডাকতে চায়।
অন্তরঙ্গতা বলতে আমি শারীরিক অন্তরঙ্গতার কথা বলিনি। আমরা যখন ছোটো ছিলাম, যে বাঙালি মধ্যবিত্ত শিক্ষিত মানসিকতার মধ্যে আমরা বড়ো হয়েছিলাম, তাতে মনটার দাম ছিল অনেকখানি। আগে মন, তার অনেক পর ছিল শরীরের স্থান। মনের অন্তরঙ্গতার অনেক পরে শারীরিক অন্তরঙ্গতার কথা উঠত। কাউকে মনে মনে ভালো না বেসে তার শরীরের সঙ্গে অন্তরঙ্গতার কথা স্বপ্নেও ভাবা যেত না। কিন্তু সারাপৃথিবীতে এই প্রায়োরিটি রিভার্সড হয়ে গেছে। এখানে শরীরের অন্তরঙ্গতা খোলমকুচির মতো সস্তা। কেউ কাউকে স্বল্প আলাপেই বিয়ার অফার করে বলে, উড ড্য হ্যাভ দ্যা বিয়ার বিফোর অর আফটার?
অর্থাৎ আদর খাওয়ার আগে বিয়ারটা খাবে, না পরে?
এই মানসিকতার যা অবশ্যম্ভাবী ফল তাই-ই ফলেছে। স্ত্রী-পুরুষ হই-হই করছে, খাচ্ছে দাচ্ছে, একসঙ্গে হুট করে বিছানায় শুয়ে পড়ছে কিন্তু এই বহির্মুখিনতার মধ্যে দিয়ে তারা একে অন্যের মন থেকে ধীরে ধীরে বড়ো দূরে চলে আসছে। প্রত্যেকে এক-একটি দ্বীপের মতো বিচ্ছিন্ন হয়ে আসছে। মনের বন্ধুত্ব বা ভারতবর্ষে ভালোবাসা বলতে যা বুঝি আমরা, এখনও যা বুঝি; তা থেকে ওরা বহুদূরে। তাই ওরা এত একলা, নির্জন; দুঃখী। সব থেকেও ওরা হাহাকার করে।
সবচেয়ে দুঃখ হয় এই কথা ভেবে ও দেখে যে, আমাদের দেশের অল্পবয়েসি ছেলে মেয়েরা হঠাৎ সাহেব-মেম হয়ে উঠতে তৎপর হয়েছে, বিশেষ করে সচ্ছল ঘরে। যে মুহূর্তে পশ্চিমিরা প্রাণপণে ভারতীয় হবার চেষ্টা করছে–ওদের প্রাচুর্যের মধ্যের হাহাকারে অভিশপ্ত হয়ে ওরা যখন আমাদের পারিবারিক জীবন, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক, বাবা-ছেলের সম্পর্ককে দারুণভাবে শ্রদ্ধা ও ঈর্ষা করছে ঠিক সেই মুহূর্তেই আমাদের যারা ভবিষ্যৎ সেই যুবসমাজ উঠে পড়ে লেগেছে। ওদের নকল করার জন্যে।
সাপ যে খোলস ফেলে যায় অতীতের গুহার ভেতরে, সেই খোলস গায়ে পরলেই তো সাপের চিকন শরীরের অধিকারী হওয়া যায় না। অন্যের অন্তঃসারশূন্য খোলসের প্রতি আমাদের এই জঘন্য আকর্ষণ : যা স্বদেশি নয়, আমাদের কৃষ্টি ও সভ্যতার পরিপূরক ও সমগোত্রীয় নয়, সেই সব ফোরেন জিনিসের প্রতি আমাদের এই দুর্বার ও ন্যক্কারজনক লোভ বড়ো লজ্জাকর মনে হয়।
সব জাতেরই দোষগুণ থাকে। নিজেদের গুণটাকে অটুট রেখে যদি দোষটাকে বর্জন করে নিজেদের মার্জিত করতে পারি আমরা, তাহলে ভারতবর্ষের মতো দেশ ও জাতি পৃথিবীতে বিরল হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। একথাটা কী করে সকলে ভুল যাই জানি না যে, আমাদের শিক্ষা-সংস্কৃতি বিজ্ঞান ওষধি এবং অনেকানেক জিনিস ওদের চেয়ে বহুদিন আগে অনেক বেশি উন্নত ছিল। মাঝে লালমুখো গুফো ইংরেজরা আমাদের গড সেভ দ্য কিং শিখিয়ে ওরা ভগবান আর আমরা নেটিভ নামক এক মনুষ্যেতর জন্তু একথাটা আমাদের মগজে ঢুকিয়ে দিয়েছিল।
অনুকরণপ্রিয়তায় এবং আত্মবিস্মরণে বাঙালি জাতির মতো বড়ো বোধহয় আর কেউই নয়। বাঙালিরা সাহেবদের সান্নিধ্যে সবচেয়ে প্রথম এসে সাহেব হয়ে গর্বিত বোধ করেছিল। তারা সবচেয়ে আগে ব্যারিস্টার, ডাক্তার প্রফেসার এঞ্জিনিয়ার আই সি এস হয়েছিল বলেই তাদের মনে এই বদ্ধমূল ধারণা জন্মেছিল যে, তারা ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ জাত। এ-ধারণা যে কত বড়ো ভুল তা প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু এখনও আমাদের গুমোর ভাঙেনি।
আমি ভারতবর্ষকে ভালোবাসি, বাংলাকেও ভালোবাসি। আমি বাঙালি বলে বাঙালিদের সম্বন্ধে আমার গর্বের অন্ত নেই। কিন্তু শুধু গর্ব চিবিয়ে খেয়ে কোনো জাতি বা প্রজাতিই বেঁচে থাকতে পারে না। এখনও যদি আমাদের দৃষ্টি স্বচ্ছ না হয়, এখনও যদি আমাদের মিথ্যা দম্ভ ও অহংকার আমরা ত্যাগ না করতে পারি, এখনও যদি রবীন্দ্রনাথ সুভাষচন্দ্র ভাঙিয়ে আমরা চালিয়ে যাব বলে মনে করে থেকে থাকি তাহলে এর চেয়ে বড়ো ভুল আর নেই বললেই চলে।
এই প্রজন্মে আন্তর্জাতিক বাঙালি বলতে সত্যজিৎ রায় ছাড়া আর কারও নাম করা যায় বলে আমার মনে হয় না। কিন্তু মুষ্টিমেয় কয়েকটি অসাধারণ প্রতিভা তো একটা প্রজাতির কলঙ্ক, অন্ধতা ও শ্রমবিমুখতার গ্লানি মুছে দিতে পারেন না। যে-স্কুলে প্রচুর ছেলে ফেল করে অথবা থার্ড ডিভিশনে পাস করে কিন্তু যে-স্কুলে একজন দুজন ছেলে স্ট্যাণ্ড করে সে স্কুলের চেয়ে যে-ইস্কুলে কেউ স্ট্যাণ্ড না করেও প্রায় সকলেই মোটামুটি ভালো ফল করে উত্তীর্ণ হয়, সেই স্কুলকে অনেক ভালো স্কুল বলে মনে করা উচিত। আমরা হচ্ছি প্রথম স্কুলের ছাত্র। গড়পড়তা বাঙালির মতো ঈর্ষাকাতর, শ্রমবিমুখ, বক্তৃতাবাজ লোক কম দেখা যায়। তবু মাত্র দু-একজন স্ট্যাণ্ড করা ছাত্র নিয়ে আমাদের আত্মশ্লাঘার শেষ নেই। এটা বাঙালির বড়ো দুর্দিনের সময়। এখনও হয়তো সময় আছে আত্মবিশ্লেষণের।
যাকগে, কী বলতে বসে কী বললাম। পাঠক ক্ষমা করবেন। বাংলা ও বাঙালিকে ভালোবাসি বলেই আমাদের এই দৈন্য ও উদাসীনতা আমাকে বড়ো পীড়িত করে। কেউ যদি আমার এই উপরোক্ত মন্তব্যে আঘাত পান, তাহলে আমি দুঃখিত হব। আমি জানি, আমার এই বক্তব্যকে ধূলিসাৎ করে সম্পাদকের দপ্তরে অনেক জ্বালাময়ী চিঠিও আসতে পারে। কারণ সেটাও বাঙালির চারিত্রিক প্রকাশ। নিজের নিন্দা বাঙালি মোটে সহ্য করতে পারে না। অন্যকে না জেনেই, অন্যের সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র ঔৎসুক্য না রেখেই নিজেকে নিজে বাহবা দেবার মতো এমন নিরেট নিবুদ্ধি শ্লথমস্তিষ্ক জাত জগতে বিরল। বাঙালির অকারণ উচ্চমন্যতা এ জাতির সব গুণকে রাহুর মতো গ্রাস করেছে।
ক্যারল আর জেনির সঙ্গে আলাপ হতেই আমি ক্যারলকে বললাম, ক্যারল তুমি বড়ো বেশি ইমোশনাল। খুব দুঃখ পাবে জীবনে তুমি।
ক্যারল স্যুপের প্লেটে চামচ নামিয়ে বড়ো বড়ো সুন্দর চোখ তুলে অবাক গলায় বলল, হাউ ডু উ্য মিন?
আমি বললাম, আজ সকালে তুমি যখন বাসে উঠছিলে তখন তোমার চোখে জল দেখেছিলাম।
তারপরই বললাম, ছেলেটির নাম কী? ক্যারল বলল, জন।
পরক্ষণেই বলল, আই লাভ হিম ডিয়ারলি।
আমি হাসলাম। বললাম, জানি।
তারপরই বললাম, তোমার পাশে-বসা এই বন্ধুটি কিন্তু একেবারে অন্যরকম। ও জীবনে প্রচুর লোককে দুঃখ দেবে কিন্তু নিজে দুঃখের ধারকাছ দিয়েও যাবে না।
জেনি মনোযোগ দিয়ে সুপ খাচ্ছিল। আমার কথা ভালো করে শোনেনি।
কিন্তু ক্যারল মাই গড বলায় ও ওর ঘন নীল দুষ্টু-দুষ্টু চোখ দুটি তুলে আমাদের দিকে তাকাল।
অবাক হয়ে বলল, কীসের আলোচনা হচ্ছে?
ক্যারল জেনিকে বলল, লুক জেনি। হিয়ার ইজ অ্যান ইণ্ডিয়ান ফেস রিডার। হি ইজ অ্যানক্যানি।
তারপর ক্যারল আমায় বলল, তুমি জেনি সম্বন্ধে যা বলেছ তা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি।
আমি বললাম, আর তোমার সম্বন্ধে?
ও মুখ নামাল। দেখলাম বড়ো বড়ো চোখের পাতার নীচে জল টলটল করছে।
আস্তে লাজুক গলায় বলল, তাও সত্যি।
জনের সঙ্গে বিচ্ছেদের কষ্টটা ক্যারল এখনও সামলে উঠতে পারেনি।
আমি বললাম, তুমি লজ্জিত হোচ্ছ কেন? ভালোবেসে কি সবাই কাঁদতে পারে? যে পারল না সে তো ভালোবাসার স্বর্গীয় আনন্দ থেকেই বঞ্চিত হল।
বলেই আমি একটা উর্দু শায়েরি আউড়ে দিলাম।
ঈ ঈশক নহী হ্যায়, ঈয়ে এক আগকা দরীয়া হ্যায়, যিসমে ডুবকে জানা হায়।
তর্জমা করে শোনাতেই ওরা উঁহু উঁহু করে উঠল।
অন্য সকলে ডিনার খেয়ে উঠে চলে গেল।
ওরা আমাকে ছাড়ল না। বলল, বোসো বোসো, তোমার সঙ্গে আলাপ হয়ে এত খুশি। হলাম আমরা। যে ক-দিন আছি তোমার সঙ্গ ছাড়ছি নে।
তারপর ক্যারল বলল, তুমি কী করো?
আমি বললাম, আমি একজন লেখক।
ইংরিজিতে লেখো?
না, বাংলায়। আমার মাতৃভাষায়।
জেনি বলল, ক্যারল খুব সাবধানে থাকিস। লেখকেরা শুধু ফেসরিডারই নয়। কখন কার সম্বন্ধে লিখে দেবে, কাকে গাছে চড়াবে, কার মই কেড়ে নেবে বিশ্বাস নেই।
আমরা সকলেই হেসে উঠলাম জেনির কথায়।
ওদের সঙ্গে সেদিন নানারকম গল্প হল। ভারি ভালো, সভ্য শিক্ষিত মেয়ে দুটি। অস্ট্রেলিয়ান।
আমাকে লেখক পেয়ে ওরা কত যে কতরকমের প্রশ্ন করতে লাগল আমায় সে বলার নয়। কখন লেখো? কী করে লেখো? প্লট আগে ভাবো না লিখতে লিখতে ভাবো? লেখার মধ্যে তুমি নিজে ছড়িয়ে থাকো না সম্পূর্ণ অনুপস্থিত থাকো? ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি।
জেনি বলল, ঊ্য আর গড।
আমি শুধোলাম, কেন?
ও বলল, এসে অবধি আমার মাকে একটা এয়ার-লেটার লিখে উঠতে পারিনি। একপাতা লিখতে গায়ে জ্বর আসে। আর তোমরা কী করে এত এত পাতা লেখো জানি না। এ ভগবানসুলভ ব্যাপার।
ক্যারল বলল বা :, উনি কি আর হাতে লেখেন, নিশ্চয়ই টাইপ করেন বা ডিকটেশান দেন।
আমি বললাম, না। বাংলা লেখা হাতেই লিখতে হয়। প্রায় সব লেখকই তাই লেখেন।
পরদিন ভোরে বেরিয়ে আমরা লেক ব্রেঞ্জ-এর পাশ দিয়ে চলতে লাগলাম। পথের ডানদিক দিয়ে একটা ঝরনা বয়ে যাচ্ছিল। এই ঝরনাটাই আয়তনে বেড়ে পরে সীন নদী হয়েছে–ফ্রান্সের। একথা নিশ্চয়ই সকলেই জানেন যে, ইয়োরোপের বেশির ভাগ নদীই সুইটজারল্যাণ্ডের উঁচু পাহাড় শ্রেণিতে জন্মেছে।
দেখতে দেখতে আমরা ব্রুনিগ পাস পেরিয়ে এলাম। এই পাসটি মাত্র দু-হাজার ফিট উঁচু। তারপর বিকেল নাগাদ পৌঁছোলাম এসে পিও পাসে। এই পাসটি ইয়োরোপের পাসগুলির মধ্যে রীতিমতো উঁচু পাস। ছ-হাজার ফিট। পিও পাসে পৌঁছোবার অনেক আগে থেকেই বরফ পড়ছিল। যতই ওপরে উঠছিলাম ততই বরফ পড়ছিল। বরফে বরফে পথঘাট মাঠ প্রান্তর বাড়ির ছাদ, টেলিগ্রাফের পোল সব সাদা দাড়িগোঁফওয়ালা হয়ে উঠেছিল। পাহাড়গুলোর মাথা থেকে পা পর্যন্ত সাদায় সাদা। এরা যে অন্য কোনো রঙের ছিল কখনো তা বোঝার উপায় নেই আর এখন। পথটাও বরফে ঢাকা ছিল, শুধু গাড়ি চলাচলের জায়গাটা পরিষ্কার। যেহেতু তখনও বরফ পড়ছিল, আশপাশ বা পথ তখনও কাদা হয়ে যায়নি। বরফ পড়া দেখতে যেমন সুন্দর, বরফ-গলা তেমনই অসুন্দর। কাদা প্যাঁচ-প্যাঁচ গা-ঘিনঘিনে একটা অনুভূতি।
ঠিক পাসের ওপরের মালভূমিতে একটা রেস্তোরাঁ, স্কি ক্লাব। স্কি-লিফট চলে গেছে পথের মাথার ওপর দিয়ে দূরের পাহাড়ে। লিফট-এ বসে খেলাশেষের পরিশ্রান্ত লোকেরা রঙিন পোশাকের কলার তুলে ফিরে আসছে। যাচ্ছে, কফি বা ব্র্যাণ্ডি খেয়ে গা-গরম করা টাটকা মানুষের দল। ছেলে-মেয়ে সকলে। এই অঞ্চলটা সুইটজারল্যাণ্ডের অন্যান্য বহু জায়গার মতো স্কিইং-এর স্বর্গ। পিও পাসের একটা বিশেষ ভূমিকা আছে। সুইটজারল্যাণ্ডের কোনো নিজস্ব ভাষা নেই যে তা অনেকেই হয়তো জানেন না। কিছু লোক জার্মান বলে, কিছু ফ্রেঞ্চ। অন্যান্য ভাষাভাষী লোকও যে নেই এমন নয়। আমরা যেদিক থেকে এলাম সেদিকে জার্মানের চল। পিঁও পাস পেরুলেই ফ্রেঞ্চই প্রধান ভাষা। এককথায় বলতে গেলে পিঁও পাস সুইটজারল্যাণ্ডের ফ্রেঞ্চ ও জার্মান ভাষাভাষী অঞ্চলের বিভাজক। এখানের রেস্তোরাঁয় চা খেলাম। নাম কল দ্যু পিও। এককাপ চায়ের দাম নিল-দেড় সুইস ফ্রাঁ।
পিঁও থেকে নামতে না নামতেই আমরা একেবারে দ্রাক্ষা-দেশে এসে পৌঁছলাম। কী আঙুর কী আঙুর! দু-দিকে শুধু আঙুর। ফ্রান্সের সীন নদীর উপত্যকা আঙুর উৎপাদনের জন্যে পৃথিবী বিখ্যাত। এখনই আঙুর তোলা হবে। থোকা থোকা ঝুলে আছে গাছে গাছে ওপাশের ঢালে এপাশের পাহাড়ি চড়াইয়ে। বেশির ভাগই সাদা আঙুর। দু থেকে তিন-ফিট উঁচু গাছ সার সার লাগানো। সারাপৃথিবীতে যে ফ্রেঞ্চ কনিয়াক ও ব্র্যাণ্ডির সমাদর তার অনেকখানি আসে দ্রাক্ষাকুঞ্জ থেকে। আঙুর; শুধুই আঙুর, যতদূর চোখ যায়।
বলতে ভুলে গেছিলুম, লাঞ্চ খেয়েছিলাম, ইন্ট্যারল্যাকেন-এ। পিও পাসের অনেক ওপাশে –সুইটজারল্যাণ্ডের জার্মান ভাষাভাষী অঞ্চলে। ইন্টারল্যাকেন জায়গাটি বড়ো সুন্দর। গ্রামের মধ্যে দিয়ে সুন্দর একটি খাল বয়ে গেছে। অনেক বাড়ি আছে খালের এপার ওপার জুড়ে মধ্যে পুরোনো দিনের কাজকরা কাঠের সাঁকো। অমিত রায় লাবণ্যর কথা মনে পড়ে গেল। হঠাৎ। কাঠের লকগেটও আছে গ্রামের মাঝামাঝি। কাঠ খোদাই করে নানারকম মূর্তি বানানো হয়। অনেক দোকান আছে সরু পথটার দু-পাশে। ট্যুরিস্টরা শপিং করতে নামেন। দা-ভিঞ্চির দ্য লাস্ট সাপার-এর একটি উড-কার্ভিং রাখা ছিল এক দোকানের শো-কেসে। দাম দু হাজার সুইস ফ্র্যাঙ্ক। শীত করছিল। দাম দেখে গা গরম হল। গা গরম হওয়ার মতো মূর্তিও ছিল অনেকানেক।
কারুশিল্প; নানা মিডিয়ামে ও নানা বেস-এর ছবি, মৃৎশিল্প; কাঠের কাজ এসব নাকি ফ্রান্সের মতো কোথাওই নেই। এমনকী ফ্রান্সকে দূর-ছাই করা ইংরেজরাও একথা স্বীকার করে, শুধু স্বীকার করে তাই নয় এটা আমাদেরও শিখিয়ে ছিল, এই জ্ঞানটা গিলিয়েছিল ঝিনুকে করে পরাধীনতার শৈশবে। কেন এ বাবদে ফ্রান্সকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্বীকার করেছিল ইংরেজরা, তার প্রধান কারণ হিসাবে মনে হয়, অস্বীকার করলে নেটিভ ভারতীয়দের উৎকর্ষের কথাই স্বীকার করতে হত।
ফ্রান্স শিল্প-সংস্কৃতির জাত নিঃসন্দেহে। কিন্তু তাদের শিল্প-সংস্কৃতির সঙ্গে আমাদের শিল্প সংস্কৃতি হেসে খেলে টেক্কা দিতে পারে। তবে ফ্রান্সের ভালোত্ব এইখানে যে, ওরা নিজেরা গুণী বলে হয়তো আমাদের এ বাবদের গুণের কদর কিছুটা করতে পারে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের গ্রামে গ্রামে জঙ্গলের আদিবাসীদের বাড়ির দেওয়ালে দেওয়ালে মুসলমানি আমল ও হিন্দু আমলের বিভিন্ন সময়ে এই সমস্ত শিল্পের যেরকম উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল তা অন্য যে কোনো দেশেরই ঈর্ষার কারণ।
আমরা প্রতীচ্যর লোক বলেই হয়তো আমাদের রুচিটা অন্যরকম। রঙের প্রতি আকর্ষণ; রঙ-বাছাই; ফর্ম; একসপ্রেশন এসবই আমাদের আলাদা ওদের থেকে। যে কারণে, ধরা যাক কাজাঘিস্থানের কনসেপ্ট অফ বিউটির সঙ্গে আমাদের কনসেপ্ট যতটা মেলে ততটা হয়তো ইয়োরোপীয় ও আমেরিকান কনস্পেটের সঙ্গে মেলে না।
সাহস করে একটা কথা বলেই ফেলি। ধরা যাক পাএল পিকাসোর কথা। স্পেশ্যালাইজড আর্টের সমস্ত সম্পর্ক বিবর্জিত এমন কোটি কোটি ভারতীয় আছেন যাঁরা ছবি বোঝেন না, মর্ডান আর্ট তো বোঝেনই না, তাঁদের কাছে পিকাসো নিশ্চয়ই একটি না-ভালো-লেগে বিস্মিত হবার ব্যাপার। আমার দৃঢ় প্রত্যয় যে, শিল্পের এই শাখা সম্বন্ধে কিছু না বুঝেও কিন্তু কোনো ভারতীয় প্রথম শ্রেণির আর্টিস্টের কাজ তাঁদের ভালো লাগবে। ব্যাপারটা একটু গোলমেলে কিন্তু এইখানেই সহজাত রুচি, রঙের প্রতি পক্ষপাতিত্ব ইত্যাদি ফ্যাক্টরগুলি এসে পড়ে। মডার্ন আর্ট না বুঝেও রঙের সঙ্গে রং মিলিয়ে গতি স্থিতি ভবিষ্যৎ বিস্মৃতি ও বক্তব্য মিশিয়ে যে-ছবি তৈরি করেন ভারতীয় শিল্পীরা তা ভারতীয়দের অধিকাংশরই ভালো লাগে। রঙের ভালোলাগার জন্যে। যে কারণে জাপানি চিত্রকরদের ওয়াশের কাজ একজন গড়পড়তা ভারতীয়র যতখানি ভালো লাগে ততখানি ইয়োরোপীয় মডার্ন আর্ট হয়তো লাগে না। ইউরোপীয় যে আর্টের প্রতি ভারতরীয়দের সহজাত দুর্বলতা তাতে রঙের আধিপত্য একটা বড়ো ব্যাপার। যে কারণে ইয়োরোপীয় ইম্প্রেশনিস্ট আর্টিস্টরা একজন সাধারণ ভারতীয়র কাছে জনপ্রিয়। প্রথমত তাঁদের ছবি বোঝা সাধারণের পক্ষে সহজ, দ্বিতীয়ত রঙের প্রয়োগ ও সাযুজ্য ভালো লাগে বলে।
উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি, ভ্যানগগ এবং গঁগা। এঁদের ছবির সহজ বোধগম্যতা এবং রঙের প্রাণবন্ততা সাধারণ আমাদের কাছে খুব সহজে মন কাড়ে।
যাকগে নিজের এক্তিয়ার ও জ্ঞানবহির্ভূত জলে বেশিক্ষণ থাকা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। বিদগ্ধ সমালোচক ও প্রফেশনাল নিন্দুকদের জোঁক ও সাপ থাকে সে জলে। যা বলছিলাম, তাই বলি।
ইন্টারল্যাকেনে যে রেস্তোরাঁটাতে আমরা খেলাম তার সামনে দিয়েই সেই খালটি বয়ে গেছে। আমি বলছি খাল; সেটা হয়তো নদী। কী নদী খেয়াল করে জিজ্ঞেস করিনি। নানারকম হাঁস, গাডওয়াল, পেপাচার্ড, পিনটেল, সাইবেরিয়ান ও অস্ট্রেলিয়ান রাজহাঁস ইত্যাদি ভেসে বেড়াচ্ছে তাতে। আমার নতুন অ্যাডমায়ারার জেনি ও ক্যারল জোর করে ছবি তুলল আমার সঙ্গে খাল পাড়ে। ছবিগুলো পরে দেশে ফিরে পাই। খুব ভালো উঠেছিল ওদের ছবি। কারণ, ওরা দেখতে ভালো।
কাঠ-খোদাই-করা নানারকম মূর্তির দোকান ছাড়াও অন্য নানারকম জিনিসের দোকান ছিল ইন্টারল্যাকেনে। সুইস চকোলেটের দোকান; স্কিয়িং আউটফিট, ঘড়ি, গ্র্যাণ্ডফাদার ক্লক থেকে খুদে রিস্ট-ওয়াচ পর্যন্ত। দেখলাম, যাঁরা এখনও কেনেননি তাঁরাও একটি করে কুকু-ওয়ালক্লক কিনলেন। প্রতি প্রহরে মুরগি বা অন্য পাখি মাথা ঝাঁকিয়ে যেসব ঘড়িতে প্রহর ঘোষণা করে সেই ঘড়ি। এ ঘড়ি একটা করে কিনে নিয়ে যাওয়া নাকি সুইটজারল্যাণ্ডে আসার প্রমাণ। আমার প্রমাণ? কোনো প্রমাণ রইল না। ভাগ্যিস ক্যারল আর জেনি অন্য কো-ট্র্যাভেলারকে ধরে ছবি তুলিয়েছিল। ইলেকট্রনিক্স ইণ্ডাস্ট্রিতে এরা প্রচন্ড এগিয়ে গেছে। অবশ্য পরে জাপানে গিয়ে বুঝেছিলাম যে এরা কিছুই এগোয়নি।
দেখতে দেখতে সন্ধের মুখে আমরা লেক জেনেভার পাশে এসে পড়লাম। স্লান সূর্যটা তখন লেক জেনেভার জলে ডুবছিল লালিমার গ্লানিমায় জল ভরে দিয়ে। লেক জেনেভা পঞ্চাশ মাইল লম্বা ও দশ মাইল চওড়া। এরই একপ্রান্তে জেনেভা অন্যপান্তে জুরিখ।
আমরা জেনেভার কাছে একটা ছোটো হোটেলে থাকব। শহরে ঢোকার আগে বাঁ-দিকে জলের মধ্যে ঐতিহাসিক সিঁওর জেলখানা। পাথরের তৈরি। আপনারা যাঁরা বায়রনের প্রিজনার অফ সিও পড়েছেন তাঁদের নিশ্চয়ই মনে পড়ে যাবে। অবশ্য বায়রনের এই বিখ্যাত কবিতাটিতে সত্যের অপলাপ আছে। কিন্তু সত্যর সঙ্গে কাব্যর প্রায়শই মিল থাকে না। সত্যর সঙ্গে গাঁটছড়া না বেঁধেও যে কাব্য তার নিজগুণে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, এমনকী সত্যকে মিথ্যায় পর্যন্ত পর্যবসিত করতে পারে এ কবিতাটি তার প্রমাণ। অথচ যাঁরা বনিভার্ডের এই বন্দিদশার পটভূমি না জানেন এবং বন্দিদশা সম্বন্ধেও না জানেন তাঁদের মধ্যে এই কবিতাটিতে বর্ণিত কথাগুলিই সত্য হয়ে থাকবে।
স্যভয়ের ডিউক চার্লসের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের জন্যে চতুর্থ চার্লস এই কারাগারে চারবছর বনিভার্ডকে বন্দি করে রেখেছিলেন। ১৫৩২ থেকে ১৫৩৬ অবধি। কবিতাটিতে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থার কথা লেখা আছে। কিন্তু আসলে বনিভার্ড মোটেই শৃঙ্খলাবদ্ধ ছিলেন না। তিনি দিব্যি হেঁটে চলে বেড়াতেন। এমনই বেড়িয়েছিলেন ওই চারবছরে দুর্গের ভেতরে যে, পাথরের ওপরে তাঁর চলাচলের পথ-চিহ্ন তৈরি হয়ে গেছিল।
আজ রাতে আমার ভাগে যে ঘরটি পড়েছিল সেটা ভারি ভালো। একটা চোট্ট ব্যালকনি, দোতলার ওপরে। লতানো গোলাপ বেয়ে উঠেছে সে-পর্যন্ত। দরজা খুলে ব্যালকনিতে দাঁড়ালেই সামনে লেক জেনেভা বহুদূর অবধি। হোটেলটা এক পাহাড়ের ওপর। সে কারণে, দোতলা হলেও মনে হচ্ছে যেন কত উঁচুতে।
রাতের আলো জ্বলে উঠেছে চারিদিকে। নীল জলে রঙিন আলোর সব প্রতিফলন পড়েছে। মাইলখানেক গিয়ে লেকটা একটা বাঁক নিয়েছে সামান্য। যত দূর চোখ যায় শুধু নীল রাতের জলে বিচিত্র রঙের প্রতিফলন। বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতে বা চেয়ার টেনে বসতে ভালো লাগে খুব। কিন্তু বেশিক্ষণ বসা যায় না ঠাণ্ডার জন্যে।
একটা ভালো লটারি পেলে মন্দ হত না। অবশ্য লটারির টাকা বিদেশে নেওয়া যেত না। যাইহোক, যদি কোনো অলৌকিক উপায়ে বেশ বড়োলোক হওয়া যেত তাহলে সুইটজারল্যাণ্ডে অস্ট্রিয়ার এরকম কোনো ছোট নিরুপদ্রব হোটেলে অথবা একটা কটেজ নিয়ে থাকতাম, বেড়াতাম; লিখতাম। কী সুন্দর জায়গা।
কিন্তু আমার দেশ ছেড়ে চিরদিনের জন্যে কখনোই বিদেশে আসতে চাই না আমি। এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবেনাকো তুমি। সত্যিই কোথায় এমন দেশ? এমন ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি, এমন ঘনঘোর বরষা, এমন মিষ্টি নরম বেড়ালছানার মতো লঘু-পায়ের শীত, এমন মহুয়ার গন্ধ-ভরা বসন্ত, এমন শিউলি-ফোঁটা শরৎ, এমন বিষণ্ণ হেমন্ত তো আর কারও নেই। আর কারও নেই এত বৈচিত্র্যও। কবে যে আমাদের দেশকে যথার্থ সম্মান দিতে পারব, কবে যে ভালোবাসাতে পারব তা জানি না। আজও আমরা নিজেদের এবং নিজেদের দেশকে চিনলাম না বলে বড়ো দুঃখ হয়।
খাওয়ার সময় হয়ে গেল। নীচে নেমে ডাইনিং রুমে গেলাম। ইয়োরোপের সব জায়গাতেই ইংরেজ মহিলাদের জন্যে মনে বড়ো কষ্ট বোধ হয়েছে। এদের সঙ্গে আমাদের মা-মাসিদের সঙ্গে এক বাবদে বড়ো একটা মিল আছে। প্রথমত, তাঁরা খাওয়ার পর অথবা সঙ্গে জল চান, দ্বিতীয়ত, সন্তান-সন্ততি যতই খারাপ হোক না কেন তাঁদের সর্বদা গুণগান করেন।
খেতে বসে প্রায়ই এরকম হত। বর্ষীয়সী ইংরেজ মহিলারা জল জল করে চাতক পাখির মতো চেঁচাতেন আর জার্মান অথবা ফ্রেঞ্চ স্টুয়ার্ড বা ওয়েটাররা সরী অথবা মেরসী বলে হৃক্ষেপ না করে চলে যেত।
ছোটোবেলায় বয়স্কাউটে শিখেছিলাম দিনে কোনো না কোনো স্বার্থহীন কাজ বা উপকার কোরো কারও না কারও। হঠাৎ শুভবুদ্ধি চেগে উঠল। চেয়ার ছেড়ে উঠে গিয়ে সোজা প্যানট্রিতে ঢুকে পাঁচ-ছ গ্লাস জল নিয়ে ট্রেতে বসিয়ে মহিলাদের দিলাম। তাঁদের সকলেরই বয়েস ষাটের ওপর। জল পেয়ে তাঁরা একেবারে পাখি সব করে রব-এর মতো কলকল করে উঠলেন। একজন ঠাকুমার বয়সি মহিলা তো এঁটো মুখে একটা চুমু খেয়েই বসলেন আমার গালে। সকলেই বললেন, তুমি আমাদের এত দেখাশোনা করছ কেন? তখন থেকেই দেখছি যে, তুমি অন্যদের মতো নও।
আমি বললাম, আমাদের দেশে সব ছেলেই মা-মাসির দেখাশোনা এমন করেই করে। বেশি কী আর করলাম।
একজন বললেন, আহা! সকলের ছেলে যদি এরকম হত। তুমি আমার নিজের ছেলের চেয়েও বেশি।
একথার জন্যে তৈরি ছিলাম না। কারণ এই মহিলাই কাল ডিনারের পর অন্য মহিলাদের সঙ্গে যখন গল্প করছিলেন, তখন আমি পাশের সোফায় বসে ম্যাগাজিন উলটোচ্ছিলাম। উনি বলছিলেন, আমার ছেলের মতো ছেলে হয় না, কারণ ওর ওয়েডিং-অ্যানিভারসারির সময়ে প্রত্যেকবার আমাকে নিয়ে যায় নটিংহামশায়ারে, বার্মিহাম থেকে। প্রত্যেক মাসে নিয়ম করে একটা চিঠি লেখে–ক্রিসমাসের সময়ে প্রত্যেকবার দামি দামি উপহার পাঠায় আর বার্মিংহামের ধারে-কাছে কোথাও কাজে এলেই নিশ্চয়ই দেখা করে যায় আমার সঙ্গে আমার রান্না ক্যাবেজ স্যুপ সে খেয়ে যাবেই যাবে। সে নাকি বলে যে, তোমার হাতের স্যুপ পেলে আমি হিলটানের রান্নাও ফেলে দিতে পারি।
আসলে ওদেশি মায়েদের প্রত্যাশা তাঁদের ছেলে-মেয়েদের কাছে এতই কম যে, ছেলে মেয়েরা একটু কিছু করলেই তাঁরা বড়ো মুখ করে সবাইকে বলেন।
খাওয়া-দাওয়ার পর মিসেস ফিনিগান, সেই চুমু-খাওয়া বৃদ্ধা আমাকে হাত ধরে নিয়ে গিয়ে সোফায় বসিয়ে আমার জন্যে একবোতল ওয়াইন অর্ডার করলেন। আমি আপত্তি করাতে বললেন, আচ্ছা! আমিও খাব তোমার সঙ্গে একটু।
তারপর সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে বললেন, আমাকে তোমার মায়ের কথা এল। কেমন দেখতে উনি, তুমি কী করো ওঁর জন্যে?
আমি লজ্জায় পড়লাম।
বললাম, আমার মা খুব সুন্দরী, ভারি ভালো, মায়ের কি আর ভালো-মন্দ হয়; মা, মাই ই। তবে করতে কিছুই পারি না মায়ের জন্যে–করা যাকে বলে।
উনি বললেন, মায়ের জন্যে করা বলতে তুমি কী বোঝো?
আমি বললাম, আমি একা নই, আমাদের দেশে মায়ের জন্যে করা বলতে সকলে এককথাই বোঝে। মায়ের দেখাশোনা, দায়িত্ব নেওয়া, ইত্যাদি ইত্যাদি। আমাদের দেশে আমরা বিশ্বাস করি যে মায়ের আশীর্বাদ ছাড়া কোনো ছেলে বড়ো হতে পারে না। যে ছেলে মা-বাবাকে না দেখে তার জীবনে কিছু হয় না।
মিসেস ফিনিগান তারপর বললেন, কিছু হওয়া বলতে তোমরা কী বোঝো? টাকা রোজগার করা?
আমি বললাম, না, তা নয়।
সৌভাগ্যবশত আমরা এখনও টাকা রোজগারের ক্ষমতার সঙ্গে মনুষ্যত্বকে মিশিয়ে ফেলিনি পুরোপুরি। মিশে যে যায়নি তা বলব না, তবু এখনও এই অন্যায় বোধটা আমাদের পীড়িত করে।
উনি বললেন, তুমি মায়ের জন্যে কিছুই করতে পারো না বললে এর মানে কী?
আমি বললাম, এই করতে পারাটা টাকা-পয়সার ব্যাপার নয়। টাকা-পয়সার দিক দিয়ে কিছু করতে পারিনি তা বলব না কিন্তু যা পেলে মা খুশি হতেন, রোজ একটু কাছে বসা, একটু কথা বলা, কখনো-সখনো তীর্থ করতে বা বেড়াতে নিয়ে যাওয়া এসব প্রায় কিছুই করতে পারিনি।
পারোনি কেন?
সময়ের অভাবের জন্যে। আমার অবকাশ বলে কোনো কিছু নেই। সময়ের অভাব ছাড়া জীবনে অন্য কোনো অভাব আমার নেই। সেজন্যেই মায়ের জন্যে যা করতে পারতাম তা করতে পারিনি।
ওয়াইনের বোতল খুলে দিয়ে গেল বারের মেয়েটি। ভদ্রমহিলা বললেন, শোনো, বলেই আমার হাতে হাত রাখলেন। গলার চামড়া, মুখের চামড়া, লোল হয়ে ঝুলে গেছে। একটা প্রিনটেড ফ্রক পরা, গায়ে একটা গরম বাদামি-রঙা চামড়ার বোতামের কার্ডিগান, গলায় ও মাথায় লাল স্কার্ফ বাঁধা। আমার হাতে যখন হাত ছাঁওয়ালেন তখন মনে হল আমি মরা মানুষের ঠাণ্ডা হাতে হাত ছোঁওয়ালাম।
আমি চমকে ওঁর মুখের দিকে চাইলাম। দেখলাম ওঁর চোখের কোণে জল কিন্তু সে জল যাতে গড়িয়ে না পড়ে সেজন্যে তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করছেন।
মিসেস ফিনিগান হাসতে গেলেন, কিন্তু কান্না চাপবার চেষ্টায় সে হাসিটা বড়ো করুণ দেখাল।
উনি বললেন, তোমাদের দেশে যাইনি কখনো, তোমরা আমাদের তাঁবে ছিলে বহুদিন। কিন্তু তোমাদের দেশ আমাদের দেশের চেয়ে অনেক বড়ো। তোমরাই একদিন আমাদের ওপর প্রভুত্ব করবে, দেখে নিয়ে। তুমি দেখো, তোমরা যা জানো, তা-ই সত্যি। মায়ের আশীর্বাদ ছাড়া কারও কিছু হয় না। আমরা বড়ো বঞ্চিত জাত। আমরা নিজেরা পাইনি তোমরা যা পেয়েছ তোমাদের মায়েদের কাছ থেকে, আমরা তাই দিতেও পারিনি আমাদের ছেলে-মেয়েদের তেমন করে।
আমি কথা ঘুরিয়ে বললাম, এটা ঠিক না। সমস্ত দেশের সামাজিক জীবন আলাদা আলাদা, সামাজিক জীবন অর্থনৈতিক মান ও জীবনের ওপর অনেকখানি নির্ভরশীল। ওভাবে বললে ঠিক বলা হয় না। আমাদেরও অনেক দোষ আছে এবং আমাদের মধ্যে সকলেই যে মাতৃভক্ত এমন নয়। আমার কথা বলতে পারি আমি।
উনি বললেন, না। আমি নিশ্চিত জানি, তোমাকে দেখেই বুঝতে পারছি যে তোমাদের দেশে মা-ছেলের সম্পর্ক কেমন।
আমি দেখলাম, এ আলোচনা ও এ প্রসঙ্গ অনেকক্ষণ চলতে পারে। তা ছাড়া মিসেস ফিনিগান যেমন ইমোশনালি ইনভলভড হয়ে পড়েছেন এই আলোচনায়, এর জের বেশিক্ষণ না টানাই ভালো।
ওয়াইন শেষ হতেই আমি উঠে পড়লাম। বললাম, আমার কিছু কাঁচাকাচি করতে হবে কাল ভোরে তো আমরা প্যারিসের দিকে রওয়ানা হব, তাই না?
উনি দুঃখিত হলেন। আমিও হলাম। হয়তো এই ওয়াইনের দাম দিলেন উনি অনিচ্ছুক ছেলের পাঠানো সাহায্যের সামান্য অঙ্ক থেকে–যে-টাকায় ভালোবাসা জড়ানো নেই, আছে শুধু বিরক্তিময় কর্তব্যর গন্ধ। সে-টাকা যাকে নিরুপায় হয়ে গ্রহণ ও খরচ করতে হয় তার পক্ষে, বড়ো গ্লানি জমে। অসহায়তার গ্লানি। সেই গ্লানির টাকা থেকে সঞ্চিত সামান্য পুঁজি ভেঙে আমাকে উনি ওয়াইন খাওয়ালেন শুধু একটু কাছে বসে গল্প করার জন্যে। যে ছেলের ভালোবাসা তিনি সম্পূর্ণভাবে পাননি অথচ হয়তো চেয়েছিলেন, তার পরিপূরক পুত্রস্থানীয় অন্য একজনকে পেয়ে তাঁর মাতৃহৃদয়ে সন্তানস্নেহ হঠাৎ উথলে উঠেছিল নিশ্চয়ই। কিন্তু আমি কী করতে পারি? নিজের মাকেই সুখী করতে পারিনি যখন, তখন অন্যের মাকে দুঃখ না হয় দিলামই।
সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠতে উঠতে আমার মায়ের কথা মনে পড়ছিল। মা সবসময়ে বলতেন, স্নেহ নিম্নগামী। ছেলে মাকে ভালোবাসুক আর নাই-ই বাসুক, মা কি ছেলেকে না ভালোবেসে পারে খোকন?
আজ আমার মা নেই। তাই অন্যের মায়ের কাছে বসে থাকলে আমার চোখও ভিজে ভিজে লাগে। আমাকে দোষী কোরো না, মিসেস ফিনিগান।
ভোরে উঠে প্যারিসের পথে রওয়ানা হলাম।
প্যারিস নামটাতেই উত্তেজনা হয়। আসলে আমাদের মতো গরিব-গুরবোরা যে কনডাকটেড টুর নিয়েছি তাতে কোনো বড়ো শহরে থাকাই আমাদের ভাগ্যে নেই। কসমস কোম্পানি পয়সা বাঁচাবার জন্যে বার্লিন, মুনিখ, জেনেভা ইত্যাদি কোথাওই রাতে রাখেননি। আগেই বলেছি যে, জেনেভা থেকে প্রায় পঞ্চাশ মাইল দূরের এক গ্রামের হোটেলে রাখা হয়েছিল আমাদের। ইনসব্রাকেও তাই।
সমস্ত বড়ো শহর বর্জন করা হলেও প্যারিসকে বর্জন করা হয়নি। কারণ প্যারিস না দেখলে ইয়োরোপ দেখার মানে নেই কোনো।
পথে একটা টায়ার পাংচার হল। ডিজোর আগে। ডিজোতে আমরা লাঞ্চ করার জন্যে থামলাম। সেখানেই জ্যাক কারখানায় নিয়ে গিয়ে টায়ার ঠিক করে নিল।
ডিজোতে যে লাঞ্চ খেয়েছিলাম অমন অখাদ্য লাঞ্চ আর কোথাওই খাইনি। সার্ভিসও অত্যন্ত খারাপ। ফ্রান্সে ঢুকলেই একটা এলমেলো অগোছালো ভাব চোখে পড়ে। মনে হয় এখানে শৃঙ্খলাবোধ-টোধ ব্যাপারগুলো বোধহয় ইয়োরোপের অন্যান্য জায়গা থেকে অন্যরকম।
আণ্ডারডান বিফ-স্টেক আর ওয়েফার চিপস দিল। সঙ্গে না স্যুপ, না সুইট ডিশ।
প্রসঙ্গত বলি, যাঁরা জানেন না তাঁদের জন্যে; (আমার এ লেখা বিজ্ঞদের জন্যে নয় আগেই বলেছি) যে বিফ স্টেক আণ্ডারডান অর্থাৎ কম সিদ্ধই খেতে ভালোবাসে শীতের দেশের লোকেরা। বোধহয় অনেকক্ষণ হজম হতে লাগে, গা গরম থাকে বলে। আমাদের পক্ষে, ওয়েল-ডান এমনকী ওভার-ডান সবই শক্ত মনে হয়। গোমাংস বলতে আমাদের ঘেন্নায় গা রি-রি করে বটে কিন্তু ওখানে গোমাংস বড়ো নরম আর উপাদেয়। লানডানে তো গোমাংসর দাম চিকেন ও পর্কের চেয়েও বেশি।
শুনেছি আমাদের শাস্ত্রেও আছে যে, চিরযুবক থাকার বিচক্ষণ উপায় হচ্ছে কচি বাছুরের মাংস গব্যঘৃত দিয়ে রান্না করে খাওয়া এবং নিজের বয়েসের অর্ধেক বয়েসের নারীর সঙ্গে সহবাস করা। যৌবন অটুট থাকবেই থাকবে। সেই হিসেবে, তিরিশ বছরের যুবার পনেরো বছরের যুবতীর সঙ্গে সহবাস করতে হবে। পঞ্চাশ বছরের যুবকের পঁচিশ বছরের যুবতীর সঙ্গে। সাধে কি আমাদের যৌবন এত দ্রুত পালিয়ে যায়! শাস্ত্রমতানুসারে ক্রিয়াকর্ম করা হয় না বলেই তো সকলের এই অবস্থা। এবং আমাদের যৌবনও ভবিষ্যতে দ্রুত কর্পূরের মতো উবে যাবে যে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।
ডিজোতে একটা মজার ব্যাপার হল। ইংরেজ আর ফরাসিদের মধ্যে যে কী ভাব, ওদের মধ্যে থেকে তা দেখতে হয়। লাঞ্চের পর পুরুষদের ল্যাভাটরিতে গিয়ে দেখি সেখানে দরজা নেই। ওয়েস্ট-কোট সাইজের একটা সুইং-ডোর লাগানো–তার নীচে দিয়ে ও সুইং-ডোর ঠেললেই সারি সারি ইউরিনাল দেখা যাচ্ছে। আর ঠিক তার বিপরীতে মেয়েদের ঘর।
বিল, প্যান্টের বোতাম খুলতে খুলতে আমার পাশে দাঁড়িয়ে সুইংডোরটার দিকে চেয়ে বলল, উ্য নো উই আর ইন ফ্রান্স নাউ। দেয়ার কান্ট বি এনি মিস্টেক বাউট দ্যাট।
সত্যি! ওই ব্যাপারটা কোথাও দেখিনি। অস্বস্তিকর তো বটেই। মেয়েরা পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। শুধু অস্বস্তিকর নয়, লজ্জাকরও বটে। অন্তত আমার তাই-ই মনে হল।
ডিজোয় খাওায়-দাওয়া সেরে আমরা আবার এগোলাম। হাইওয়ে দিয়ে। বিকেল হয়ে গেল। প্যারিসের আর বেশি দেরি নেই। দূরে ডানদিকে ওর্লি এয়ারপোর্ট দেখা যাচ্ছে। লানডানের হিথ্রোর মতোই নামকরা প্যারিসের ওর্লি। কিন্তু আরও একটি বড় ও নতুন এয়ারপোর্ট হয়েছে। চার্লস দ্য গল এয়ারপোর্ট। কিন্তু এই এয়ারপোর্টটি প্যারিস শহর থেকে দূরে বলে এখনও তেমন জমজমাট হয়নি।
সামনে কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। পুলিস প্রায় এককিলোমিটার দূর থেকে লুমিনাস লাল দিয়ে ডেঞ্জার লেখা প্লাস্টিকের সাইন পথের বাঁ-পাশে রেখে গেছে। তাই দেখে সব গাড়ি আস্তে করছে গতি। অ্যাক্সিডেন্টটা হয়েছে সামান্য আগে।
বিদেশের হাইওয়েতে যখনই অ্যাক্সিডেন্ট হয় তখনই তা হয় মালটিপল অ্যাক্সিডেন্ট। অনেকগুলো গাড়ি একে অন্যের ঘাড়ে উঠে যায় গতি সামলাতে না পেরে। এই অ্যাক্সিডেন্টে তিনটি গাড়ি জড়িয়ে পড়েছিল।
অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে সামান্য আগে, ইতিমধ্যে পুলিশ এসেছে। অ্যাম্বুলেন্স এসেছে, আহত যাত্রী ও চালকরা পৌঁছে গেছে হাসপাতালে। দুর্ঘটনায় জড়িত গাড়িগুলোকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশের গাড়ি। আরও দু-তিনটে পুলিশের গাড়ি আরও দু-দিকের রাস্তার মধ্যের পথে দাঁড়িয়ে আছে। পুলিশের গাড়ি মানে ভ্যান নয়। বিরাট বিরাট মোটরগাড়ি। এক-একটা গাড়িতে একজন অথবা দুজন করে পুলিশ থাকে। ওপরে লাল-আলো ঘোরে, সাইরেন ফিট করা থাকে গাড়িতে। ওয়্যারলেস থাকে। ওয়াকি-টকি থাকে।
কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হলে পুলিশ অ্যাম্বুলেন্স ইত্যাদি যে কত তাড়াতাড়ি এসে পড়ে এবং সব কিছুর বন্দোবস্ত করে তা বলার নয়। আমাদের দেশে নিজের কাজ এখনও যত না আমরা করি ভলান্টিয়ারিং করে পরের ব্যাপারে দৌড়ে যাই তার চেয়ে বেশি। কিন্তু ওখানে সমস্ত সামাজিক দায়িত্বগুলো অত্যন্ত স্পেশালাইজড হয়ে পড়েছে। এর মধ্যে একটা হৃদয়হীনতা অথবা হৃদয়বত্তার ব্যাপার আছে। যে যেমন ভাবে দেখবেন। পথের পাশে গাড়িতে রক্তাক্ত অবস্থায় কেউ পড়ে আছে তাকে তুলে নিয়ে হাসপাতালে যাওয়ার হলে ওরা যাবে কি যাবে না, জানি না। কেউ যাবে, কেউ যাবে না। তবে খামোখা মজা দেখতে ভিড় বাড়াতে আর উঁহু-আহা করতে হাজার লোক জমায়েত হয়ে পুলিশ আর অ্যাম্বুলেন্সের কাজের বিঘ্ন ঘটাবে না। ঘটাবে না প্রথমত, এই কারণে যে, ওরা প্রত্যেকে বড়ো বদ্ধ জীবনযাপন করে, এবং দ্বিতীয়ত, ওদের প্রত্যেকের সময়ের দাম আছে।
প্যারিসে ঢুকে মনে হয় কলকাতায় ঢুকলাম। মানে মেজাজের ব্যাপারে। আড্ডা-গুলতানি, সিনেমা, থিয়েটারের লাইন, বেপরোয়া এবং আইনকে থোড়াই-কেয়ার করে এমন গাড়ি চালানো ইয়োরোপের কোথাওই দেখা যায় না। ইয়োরোপের কোনো বড় শহরের পথঘাটে এমন আকছার আবর্জনা ও কাগজপত্র পড়ে থাকে না। কোনো শহরই রাতে আর দিনে এমন করে জীবন্ত হয়ে বেঁচে থাকে না।
যে ক-দিন প্যারিসে ছিলাম, যদিও অত্যন্ত সামান্য দিন, কিন্তু সে ক-দিনে একথাই মনে হয়েছে বার বার যে প্যারিসের সঙ্গে কলকাতার কোথায় যেন একটা দারুণ আত্মিক যোগ আছে। মানসিকতার দিক দিয়ে, সাহিত্যরসের ব্যাপারে, শিল্পকলা সম্বন্ধে ঔৎসুক্যর ব্যাপারে এবং কুঁড়েমি, আজ্ঞা ও বৈষয়িক ব্যাপারকে আপেক্ষিক কম গুরুত্ব দেওয়ার বাবদে এই দুই শহর বলতে গেলে যমজ বোন। সিনেমার টিকিটের লাইনে মারামারি প্যারিস ছাড়া কোনো ইয়োরাপীয় শহরে এমন আকছার দেখ যায় না।
প্যারিসের সাঁসে-লিজায় যেখানে সেরেমোনিয়াল প্যারেড হয় উৎসবে-টুৎসবে, দ্য গল স্কোয়ারে যেমন বেহিসাবি ও দায়িত্বজ্ঞাহীনতার সঙ্গে গাড়ি চালানো হয়, কোথাওই বোধহয় হয় না। আমাদের কলকাতার চৌরঙ্গীর কথা মনে পড়ে। উপমাটা অবশ্য সমুদ্রের সঙ্গে ডোবার হল–আয়তনের দিক দিয়ে রাত নটায় আমরা প্যারিসের একবারে বুকে কোরকে এসে পৌঁছোলাম।
সেন্ট মার্টিন ক্যানাল বরাবর আমরা এগিয়ে গেলাম। প্যারিসের শহর-সীমা নির্ধারণ করে একটা সার্কুলার রাস্তা আছে। আগে একটা দেওয়ালও ছিল। এখন দেওয়ালটা ভেঙে দিয়েছে। প্যারিসে প্রচুর পাথরের রাস্তা আছে, মানে যাকে কবলড রোড বলে। আজকালকার দিনে কলকাতার স্ট্র্যাণ্ড রোডের মতো এমন রাস্তা সচরাচর কোনো বড়ো শহরে দেখা যায় না। আগে যখন ঘোড়ার গাড়িই প্রধান বাহন ছিল মানুষের তখন অবশ্য সব জায়গাতেই এইরকম। রাস্তাই ছিল। কংক্রিট ঢালাই করা বোধহয় মানুষ তখনও শেখেনি। অত পুরোনো রাস্তা কিন্তু তার অবস্থা আশ্চর্যজনক ভালো দেখে বিস্মিত হতে হয়।
সীন নদীর ধারে একটা সরু গলিতে হোটেল অ্যাভিয়েটর বলে একটা ছোটো হোটেলে এসে উঠলাম আমরা। অনেক তলা হোটেল, কিন্তু লিফট নেই। সরু সিঁড়ি। শুধু ঘর ভাড়া দেয় এরা আর ব্রেকফাস্টের বন্দোবস্ত আছে। খাওয়া-দাওয়া নেই। বার আছে অবশ্যই। প্যারিসের হোটেল অথচ বার নেই, ভাবা যায় না।
ঘরে ঢুকেই যা প্রথমে চোখ পড়ল বাথরুমে, তা বিদে। ফরাসিরাই এর প্রথম আবিষ্কর্তা। বিদে এখন এদেশেও তৈরি হচ্ছে। আপনারা অনেকেই হয়তো ফাইভ স্টার হোটেলের বাথরুমে ঢুকে একটা অদ্ভুত দর্শন কমোডের মতো ব্যাপার দেখে হকচকিয়ে যান জিনিসটা কী অনেকেই তা জানেন না। বিদে শুধুমাত্র মেয়েদের ব্যবহারের জন্য। মেয়েদের ব্যক্তিগত অনেক ব্যাপারে বিদে বিশেষ সুবিধাজনক। ফরাসিরা যে অত্যন্ত শিক্ষিত জাত তা মেয়েদের সুখ-সুবিধে নিয়ে তাদের বহুকাল আগে থেকে এই ভাবনা সেটাই প্রমাণ করে।
পাছে অশিক্ষিত ইংরেজ পুরুষ বিদে নিয়ে কী করবে ভেবে না পান, তাই তাদের জ্ঞাতার্থে বিদের ওপর ইংরিজিতে লেখা আছে দিস ইস ফর দ্য ইউজ অফ লেডিজ ওনলি। ইট ইজ নট আ কমোড আইদার।
সেদিন রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর ইলিউমিনেশন ট্যুরে বেরোনো গেল। প্যারিসের রাত সত্যিই দেখার মতো। দিনটাই রাত কি রাতটাই দিন বোঝা মুশকিল। বার রেস্তোরাঁ কাফে সিনেমা নাইট-ক্লাব থিয়েটার ইত্যাদি আরও কত কিছু জয়েন্ট আলোয় আলোময়।
এই কনডাকটেড ট্যুরের শহর দেখা আমার মোটেই ভালো লাগে না। ন্যাশানাল পার্কে জানোয়ার দেখার মতো বাসের মধ্যে বসে পূর্বনির্ধারিত ও পূর্বনির্দিষ্ট পথে পথে ঘুরে ঘুরে গাইডের মুখনিঃসৃত বাণী শুনে শহর দেখা বা চেনাতে কেমন ঠাকুরদার হাত ধরে নাতির বেড়াতে বেরোনোর গন্ধও আছে। একা একা মনেমৌজি বেড়ানোতে যে আনন্দ তাতে দলবদ্ধ পূর্বনির্ধারিত বেড়ানোর আরামে নেই।
অবশ্য দুঃখও আছে। পরদিন বুঝেছিলাম।
সাঁসে-লিজায় আবারও গেলাম। রাতের অন্ধকারের বুক চিরে হাজার হাজার সারি সারি গাড়ির হেডলাইট আলোয় আলোকিত করে ছুটে আসছে একদিক থেকে আর সারি সারি নরম লাল টেইল-লাইট সুন্দর এক দিগন্ত বিস্তৃত লালের প্যাটার্ন গড়ে চলে যাচ্ছে। সাঁসে লিজার মতো চওড়া ও বহু লেন-বিশিষ্ট পথ পৃথিবীর খুব বেশি জায়গায় নেই।
কথাবার্তায় যা জানা গেল তাতে ফরাসিরাও যে আমাদের মতো হিরো ওরশিপিং-এর জাত সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ রইল না। হয়তো এর কারণটা এই-ই যে দু-জাতই বড়ো ভাবপ্রবণ। কাউকে মইয়ে চড়াতে দেরি হয় না, মই সরিয়ে নিতেও না। তবে যখনই যা করে তা প্রবল আন্তরিকতা ও উৎসাহের সঙ্গে। মইয়ে চড়িয়ে ওপরে তুলে তারপর মই যথাস্থানে যাদের বেলা এরা সসম্মানে রেখেছে তা এ পর্যন্ত নেপোলিয়ন ও দ্য গলের বেলায়। মনে হয় এদের রাজনৈতিক মনোজগতে খুব রঙিন চমকপ্রদ স্বদেশীয়তায় বিশ্বাসী ও চটকদার লোক ছাড়া কেউ তেমন দাগ কাটে না। নইলে নেপোলিয়নের পর এত নেতা এসেছেন গেছেন কিন্তু দ্য গলকে যে সম্মানের আসনে ফ্রান্স বসিয়েছে তেমন সম্মান খুব কম লোকের জন্যেই জুটেছে। নেপোলিয়নের পরই বেবাক সমুদ্র। পরের দ্বীপ দ্য গল। আলি সাহেবের ভাষায় বললাম।
সারাশহর ঘুরে দেখতে দেখতে রাত হল অনেক। আগামীকাল আমাদের নাইট-ক্লাব ট্যুর। ক্যান-ক্যান ডান্স, শ্যাম্পেন খাওয়া–পৃথিবীবিখ্যাত প্যারিসিয়ান নাইট ক্লাবের নাচ-গান। সকালে কোনো প্রোগ্রাম নেই যূথবদ্ধতার। এইটে ভেবেই ভালো লাগতে লাগল। দেরি করে ঘুম থেকে ওঠা যাবে বহুদিন পর। ঘুম ভাঙার পরও কিছুক্ষণ আলস্যে শুয়ে থেকে কিছু ভাবা যাবে। তারপর নিজের ইচ্ছেমতো ঘুরে-ঘারে দেখা যাবে শহরটাকে। রোদটাকা পথে ওপেন এয়ার কাফেতে বসে কফি খাওয়া যাবে বা ফেঞ্চ ওয়াইন। তাড়া নেই কোনো, ব্যস্ততা নেই। দ্রুতধাবমান বাস থেকে দেখা প্যারিস সর্বদা অপসৃয়মান। কাল সকালে মগজের মধ্যে চোখের লেন্সে তোলা ছবি ডেভেলাপ করে নেওয়া যাবে ধীরেসুস্থে। ভেবেই ভালো লাগছে।
কাল বিকেলে একটা ট্যুর আছে শহরের বিভিন্ন জায়গা দেখানোর। সেই ট্যুর শেষ হবে সন্ধে ছটা নাগাদ। তারপর হোটেলে চেঞ্জ-টেঞ্জ করে সাতটায় এক রেস্তোরাঁতে এসে ডিনার খেয়ে আমরা রাতের টহলে বেরোব।
ইলিউমিনেশন ট্যুর দেখে হোটেলে ফিরতে ফিরতে রাত হল। দেখি অত রাতেও জোড়ায় জোড়ায় মেয়ে-পুরুষ হোটেলের সিঁড়ি দিয়ে উঠছে নামছে। মুখে চোর-চোর ভাব। মুখ তুলে চাইছে না বিশেষ। এই হোটেলে এসে ওঠার পরই এই জায়গাটার নির্জনতা ও নদীপারের শীতার্ত দৈন্য দেখে মনে হয়েছিল এটা একটু অন্যরকম জায়গা।
সিঁড়িতে উঠতে উঠতে জেনি বলল, আই ফিল ব্যাড। দিস সিটি ইজ ভেরি নটি। আই ফিল লাইক মেকিং লাভ টু সামওয়ান টু নাইট।
আমি হেসে মাঝ-সিঁড়িতে বাও করে বললাম, মে আই? উ্য নটি গার্ল?
ক্যারল আমাকে ও জেনিকে ওর সুন্দর নরম হাত দিয়ে দুই চাঁটি মারল।
তারপর আমাকে বলল, আমার প্রথম নামে ডেকে, ডিয়ার ডিয়ার তুমি আমার সঙ্গ চাইলে পেতে পারো কিন্তু জেনির অস্ট্রেলিয়ায় ফেলে আসা বয়ফ্রেণ্ডকে তুমি দেখোনিঃ যে-কোনো প্রাইজ বুলের চেয়ে সে ষন্ডামার্কা। আর শোয়শুয়ির ব্যাপার?। মাই গুডনেস। ইটস আ ফ্রি ফর অল অ্যাফেয়ার।
তারপর জেনি এগিয়ে গেলে ফিসফিস করে বলল, জেনি ইজ আ সিলি গার্ল আদারওয়াইজ শি কুডনট হ্যাভ লাইকড বিল।
আমার ঘুম পেয়েছিল। কে বিল? কার চেহারা প্রাইজবুলের মতো? তখন তা জানার খুব উৎসাহ ছিল না। আমি বললাম, গুড নাইট। আমি আজ তোমাদের দুজনকে পাশে নিয়ে ঘুমোব। স্বপ্নে।
ক্যারল হো হ করে হেসে উঠল। হাসলে ওকে ভারি সুন্দর দেখায়। এমনিতেও।
হাসি থামিয়ে বলল, চমৎকার ব্যবস্থা। দ্যাট উড স্যুট এভরি ওয়ান ফাইন। ওনট ইট?
দরজা বন্ধ করে দাঁত মেজে জামা কাপড় ছেড়ে বিছানায় উঠে শুয়ে পড়লাম। কাঁচের জানালার ওপাশে রাতের প্যারিস পড়ে রইল। কালো পাথরে বাঁধানো রাস্তা–সীন নদী– নদীর পারের পায়ে চলা পথ। একটু এগিয়ে গিয়েই সেভাস্তেপোল বুলেভার্ড–আলোয় আলোকিত। লোকজন, হই হই, সিনেমা থিয়েটার কত মজা।
এরকমভাবে শুয়ে শুয়ে হঠাৎ নিজের জন্যে বড় কষ্ট হল। হঠাৎ যেন আবিষ্কার করলাম যে আমি বড়ো গরিব। এইভাবে ভিখারির মতো সমস্ত আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়ে দেশ দেখার কোনো মানে হয় না। কলকাতার গড়ের মাঠে ঘোড়ার গাড়ি ভরতি লাল নীল শাড়ি পরা দক্ষিণ ভারতীয় বৃদ্ধারা যখন জাদুঘরের রাস্তা পার হয় তখন আমরা যে-চোখে তাদের দিকে চেয়ে থাকি, আমাদের দিকে প্যারিসের পথের লোকেরা ঠিক সেইভাবে চেয়ে দেখছিল। যে দেশে এসেছি সেই দেশের লোকের মতো সচ্ছল না হলে পকেটে সামান্য উদ্বৃত্ত পয়সা না থাকলে, দেশ বেড়ানোর মতো বোকামি আর কিছুই হয় না। আবার কবে আসব কে জানে? আর কি কখনো সুযোগ হবে? কিন্তু যার পকেট ফাঁকা তার পক্ষে কনডাকটেড ট্যুরের গাইডের হাত ধরে থাকা ছাড়া উপায় কী?
পরক্ষণেই মনে হল এ বেড়ানোটা কি কিছুই নয়? এ কি নিরর্থক? এত দেশ দেখা, এতজনের সঙ্গে মেশা এত বিভিন্ন রীতি নীতি আচার-ব্যবহার এত বিভিন্ন মানিসকতার মানুষের সঙ্গে পরিচিত হওয়া কি কিছুই নয়? আর্থিক সাচ্ছল্য থাকলেই যে সব মানুষ সেটাকে সঠিকভাবে চালিত করতে পারে একথাও তো ঠিক নয়। তবে আমাকে যদি কেউ প্যারিসে অনেক টাকা দিত, যদি একটা লটারি জিততাম এখানে, তাহলে সকলকে দেখিয়ে দিতাম টাকা কীভাবে খরচ করতে হয়, কত সুন্দরভাবে। খরচ করাটাও একটা মস্ত বড়ো আর্ট। আমি সে আর্টে আর্টিস্ট কিন্তু দুঃখের বিষয় আমার টাকা নেই। যাদের টাকা আছে তাদের বেশির ভাগই টাকার ব্যবহার জানে না।
এই অর্থকরী ভাবনাটা সে-রাতে প্যারিসের এক দীন হোটেলের ঘরে শুয়ে আমাকে বড়ো পেয়ে বসেছিল।
ঘুম ভাঙল অনেক বেলায়। কতদিন পরে যে বেলা সাতটা অবধি ঘুমোলাম তা বলার নয়, বহুদিনের জমা ক্লান্তি যেন ধুয়ে নিল ঘুম।
ধীরেসুস্থে ঘুম থেকে উঠে মুখ-হাত ধুয়ে নীচের ডাইনিং রুমে নেমে ব্রেকফাস্ট করলাম। তারপর পথে বেরোলাম।
একটা ফলের দোকানের সামনে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। প্রত্যেকটি ফল যে কী সুন্দর করে কাগজে মোড়া তা কী বলব! যে ফল খেয়ে ফেললেই ল্যাঠা চুকে যায় তা আবার অত কায়দা করে কাগজে মোড়া কেন? ফলের আবার এত আর্টিস্টিক ডেকরেশানের কি দরকার? এরকম কোথাও দেখেছি বলে মনে পড়ল না। এমনকী সবজির দোকানেও দেখি সেইরকম। কুমড়োর মতো একটা ফল, হয়তো কুমড়োই, সাহেবদের দেশে দেখছি বলে কুমড়ো বলে বিশ্বাস হচ্ছে না, তাও কাগজে মোড়া।
এই কারণেই ফ্রান্স অন্য সব জায়গা থেকে আলাদা। স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত হবার অনেক কিছু আছে ফ্রান্সের।
আর্ট কী? এ নিয়ে অনেকানেক আলোচনা হয়েছে একাধিক সময়ে বিভিন্ন দেশের একাধিক মনীষীদের দ্বারা। এ বাবদে রবীন্দ্রনাথের একটি কথা আমার প্রায়ই মনে পড়ে। রবীন্দ্রনাথকে শান্তিনিকেতনে একজন অতিথি জিজ্ঞেস করেছিলেন আর্টের ব্যাখ্যা আপনার কাছে কী?
রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, জানালা দিয়ে ওই দেখছ রাধু মালি ক্যানেস্তারা করে জল বয়ে আনছে, ক্যানেস্তারার কানা বেয়ে জল উপচে পড়ছে–ওই হল গিয়ে আর্ট। যে-কোনো শিল্পর জন্মই হল সুপারফ্লুয়িটি থেকে। যা প্রয়োজন, তা প্রয়োজনই। প্রয়োজন-অতিরিক্তটাই আর্ট। ক্যানেস্তারা ভরতি হয়েছে বলেই জল চলকে পড়ছে। ভরতি না থাকলে উপচে পড়ার কথাই উঠত না।
এই উপামাটা বড়ো মনে লেগেছিল। কোথায় এই কথোপকথনের কথা পড়েছিলাম তাও মনে নেই, কে এই প্রশ্নকর্তা তাও আজ মনে নেই; অনেক ছোটোবয়েসে পড়েছিলাম, কিন্তু পড়েছিলাম যে সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। পাঠকদের মধ্যে যাঁদের স্মৃতিশক্তি ক্ষুরধার তাঁরা মনে করিয়ে দিলে বাধিত থাকব।
যাই হোক, প্যারিসের সকালে কুমড়োর দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথের এই উপমাটা বড়ো লাগসই বলে মনে হয়েছিল।
অনেক দূরে হেঁটে গেলাম। কোনো গন্তব্য নেই, তাড়া নেই, খাঁটি ট্যুরিস্টের মতো শ্লথ পায়ে উইণ্ডো-শপিং করতে করতে চলেছিলাম। হাঁটতে হাঁটতে একসময়ে সেভাস্তেপোল বুলেভার্ডে এসে পৌঁছে গেলাম। জমজমাট জায়গা। একটা ওপেন-এয়ার কাফেতে বসে সাদামাটা লাঞ্চ সারলাম এখানেই, অবশ্য অনেক পরে। ভাষাটা প্যারিসে বড়ো বিপত্তি ঘটায়। সেন্টজেভিয়ার্স কলেজে ফাদার জোরিস ফ্রেঞ্চ নিয়েও ছেড়ে দিয়েছিলাম বলে আমার ওপর খুব রেগে গেছিলেন। প্যারিসের পথে প্যান্টের দু-পকেটে দু-হাত গলিয়ে, হাঁটতে হাঁটতে কেন যে ফ্রেঞ্চটা তখন শিখিনি সেকথা ভেবে আফসোস হচ্ছিল।
আমার সামনে ব্রিডিট বার্দোর মতো দেখতে অবিকল একটি মেয়ে জেব্রাক্রসিং দিয়ে রাস্তা পেরোল। বার্দো কি এখন প্যারিসে? কাল রাতে বার্দোর ফ্ল্যাট দেখেছিলাম। গাইড দেখিয়েছিল।
পশ্চিমের দেশের একটা জিনিস আমার খুব ভালো লেগেছে। কলকাতার রাস্তায় শাবানা আজমি বা অপর্ণা সেন হেঁটে গেলে লোকে কী কান্ডটাই না করে। উত্তমকুমার কখনো কী লুঙ্গি পরে জগুবাবুর বাজারে কইমাছ কিনতে পারেন? না শত ইচ্ছা থাকলেও না। অপর্ণা সেন লাইট হাউসের উলটো দিকের ফুচকাওয়ালার কাছ থেকে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে ফুচকা খেতে পারেন না কখনো, তাঁর যতই লোভ হোক না কেন। কিন্তু প্যারিসের জনবহুল এলাকাতেও বার্দো ইচ্ছে করলে ম্যাগাজিনের দোকান থেকে ম্যাগাজিন কিনতে পারেন। লোকে হাঁ হাঁ করে তাঁর ওপর চড়াও হবে না। এর কারণ, এখানের সাধারণ লোকও ভাবে আমিই বা কম কেডা?
আমিও যে কম নয় একথাটা একজাতের সকলে মিলে ভাবতে পারলে নিজেদের অজ্ঞাতসারে একটা দেশ মস্ত বড়ো হয়ে যায়।
লুভরে দেখার ইচ্ছা ছিল, ইচ্ছা ছিল মালরোর সঙ্গে আলাপ করার। আরও কত কী ইচ্ছে ছিল। কিন্তু খাঁচার পাখির স্বাধীনতার ক্ষণ ফুরিয়ে এল। ঘুরে ফিরে, হেঁটে চলে; দুটোর মধ্যে হোটেলে ফিরলাম।
প্যারিসিয়ানরা প্যারিসের আণ্ডার-গ্রাউণ্ড ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম নিয়ে খুব গর্বিত। ওরা টিউব বলে না লানডানের মতো, ওরা বলে মেট্রো। একচক্কর ঘুরে আসার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু মর্তেই ভাষা না জানার জন্যে ঘুরতে ফিরতে অসুবিধা হচ্ছিল, পাতালে গিয়ে শেষে চিরতরে গায়েব হয়ে যেতে হয় এই ভয়ে মেট্রো চড়ার সাধ বুকের মধ্যেই রইল ওযাত্রা। পরে কখনো এলে দেখা যাবে।
হোটেলে ফিরে একটু জিরিয়ে নিয়ে কনডাকটেড ট্যুরে বেরোনো হল। এই ট্যুরের গাইড একটি ফরাসি মেয়ে। ওরা ইংরজেদের ঘেন্না করে বলে বোধহয় ওদের ভাষাটাও দায়ে পড়ে শেখে। ভালোবেসে নয়। তাই বুঝি তার মধ্যে একটা ঘেন্না মেশানো থাকে। তার ফলে আমাদের মতো লোকদের সেই ইংরিজি বুঝতে একটু অসুবিধে হয়।
প্রথমেই জানা গেল যে, আমরা নতরদাম গির্জায় যাব। সেই ছোটোবেলায় ঠাকুমা হাঞ্চব্যাক অফ নতদোম কিনে দিয়েছিলেন। কতদিন যে কোয়াসিমোদো আর এসমারালডাকে স্বপ্নে দেখেছি তা বলার নয়। আজ প্রথম চর্মচোখে সেই নতরদাম দেখব।
সীন নদীর পাশ দিয়ে রাস্তা–সার্কুলার রোড। নদী মানে নামেই নদী; আগেই বলেছি, আমাদের কেওড়াতলার আদি গঙ্গার মতো। এ নদীতে কোনো ক্রমে পড়ে গেলে ঝামা দিয়ে গা ধুতে হবে এমন জলের রং।
হোটেল থেকে অনেক দূর এসে তরদামের গির্জার চুড়ো দেখা গেল। এবারে পৌঁছোব আমরা নদীর ওপরে একটি সাঁকো পেরিয়ে গির্জায় পৌঁছোতে হবে। ক্রিশ্চানরা বলে পৌত্তলিকতায় বিশ্বাস করেন না। কিন্তু যিশুর মূর্তি পুজোও কি পৌত্তলিকতা নয় একরকমের? ভগবানের নিরাকার রূপ তো আকাশে বাতাসে বনে জঙ্গলে ছড়িয়ে আছেই-যার দেখার চোখ শোনার কান আছে সে তো তাঁকে নিরন্তর দেখে শোনে–তার জন্যে যিশুর মূর্তিরই বা প্রয়োজন কী?
আমি কোনোরকম পৌত্তলিকতাতেই অবিশ্বাসী। তাই যেমন কোনো মন্দিরে ঢুকি না, গির্জাতেও যাই না। দম বন্ধ হয়ে আসে ভগবানের অমন বন্দিদশা দেখে, ভগবানের জন্য কষ্ট হয়।
যখন নতরদামে পৌঁছোল বাস তখন মেয়েটি বলল আমরা এখানে ঠিক একঘণ্টা থাকব। ভেতরে ঢুকব গির্জার। এও বলল যে, যাঁরা ফ্রেঞ্চ পারফিউম কিনতে চান, তাঁরা গির্জার সামনেই একটা হলুদ সিল্কের ব্যানার লাগানো দোকান আছে, সেখানে গিয়ে কিনতে পারেন। সকলে যখন ভেতরে ঢুকল, আমি তখন সীন নদীর ধারে ধারে যেসব পুরোনো বইয়ের
দোকান দেখেছিলাম সেদিকে এগিয়ে গেলাম?
এই দোকানগুলো অবিকল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছাকাছি যেসব পুরোনো বইয়ের দোকান আছে ফুটপাথে, সেরকম। ছবি, স্ক্রল, বই, সারে সারে। ভাষা জানি না বলে বইয়ের ব্যাপারে তেমন সুবিধে করতে পারলাম না। স্কুল ও ছবি দেখে বেড়ালাম। দরাদরি করে একটা ওয়াটার কালারের ছবি ও একটা স্ক্রল কিনলাম।
বই আমার দ্বিতীয় প্রেমিকা, প্রথম প্রেমিকা প্রকৃতি। দ্বিতীয় প্রেমিকার সান্নিধ্যে এসে তন্ময় হয়ে গেছিলাম। ঘড়ি দেখে সময়মতো নরদামের সামনে এসে দেখি আমাদের অত বড়ো বাসটাকে কে বা কারা ছিনতাই করে নিয়ে গেছে। কসমস কোম্পানির আরও অনেক বাস দেখলাম কিন্তু আমাদের বাস নেই।
হায় জ্যাক; কোথা জ্যাক? হাইজ্যাক?
অন্যান্য বাসের ড্রাইভারদের জিজ্ঞেস করলাম যে আমাদের ট্যুর নাম্বার টু-টোয়েন্টির বাসটা দেখেছ? ড্রাইভারের নাম জ্যাক? তারা সব ফোর টোয়ন্টির মতো কুড-নট-কেয়ারলেস কায়দায় মাথা নাড়ল শুধু। এক প্রফেশনাল বাস ড্রাইভারের সঙ্গে কোম্পানিরই অন্য ড্রাইভারের আলাপ নেই, এমনকী নামও শোনেনি একে অন্যের, একথা ভাবাও যায় না।
শেষে সেই ফ্রেঞ্চ পারফিউমের দোকানের কথা মনে পড়ল। দোকানটাতে যে কজন মেয়ে ছিল তাদের মধ্যে কেউ কেউ ভাঙা ভাঙা ইংরিজি বলে। তাদের জিজ্ঞেস করাতে তারা বলল বাস তো অনেকক্ষণ হল চলে গেছে।
শুনে হতবাক হয়ে গেলাম। মেলা দেখতে যাওয়া ছেলের মতো তেলেভাজার দোকানের সামনে এসে শেষে হারিয়ে গেলাম!
ওরা বলল, তুমি উঠেছ কোথায়?
উঠব আর কোথায়? আমি কি আর হিলটনে উঠেছি না রিজ-এ? হোটেলের নামটা বললাম, আর লোকেশান।
ওরা আমাকে অনেক সাহায্য করল। হোটেলের নামটা টেলিফোন ডাইরেকটরিতে খুঁজে বের করে লোকশানটা ভালো করে বুঝে নিল, তারপর বলল, নো প্রবলেম, একটা ট্যাক্সি নিয়ে চলে যাও।
ট্যাক্সি ভাড়া কোথায় আমার কাছে? যা সামান্য ফ্রেঞ্চ ফ্রাঁ ছিল তা দিয়ে তো একটু আগে ছবি-টবি কিনে ফেলেছি। ওদের সেকথা বললাম।
ওরা তখন বলল, মেট্রোতে করে চলে যাও অথবা বাসে।
আমি বললাম, কক্ষনোও না। পয়সাও নেই, তা ছাড়া বাসে বা মেট্রোতে গিয়ে ভাষাবিভ্রাটে হয়তো আরও অনেকদূর গিয়ে পড়ব। ওদের শুধোলাম, আমার হোটেল নতরদাম থেকে কত দুরে?
ওরা বলল পাঁচ-ছ মাইল তো বটেই।
আমি বললাম, ফার্স্ট ক্লাস। হেঁটেই যাব।
সুন্দরী মেয়ে দুটি আমার কথা শুনে ফর্সা মুখ বেগুনি করে বলল, এল কী?
আমি বললাম, হেঁটে যাওয়া অনেক সেফ। আমার হাতে অনেক সময় আছে।
আইফেল টাওয়ার ইত্যাদির এত ছবি দেখেছি ও পড়েছি যে তা দেখা থেকে বঞ্চিত হওয়ার জন্যে কোনো দুঃখ নেই–বরং প্যারিসের পথে জনারণ্যে গা এলিয়ে এতখানি হেঁটে যাওয়া আমার কাছে অনেক আনন্দের। মনে মনে নিজেকে বোঝালাম। মনুমেন্টের চেয়ে একজন সাধারণ মানুষ আমাকে চিরদিনই অনেক বেশি আকর্ষণ করেছে।
ওরা আমাকে একটা ম্যাপ এঁকে দিয়ে বলল, সেভাস্তেপোল বুলেভার্ডে পৌঁছে তুমি সোজা এগিয়ে যাবে।
তারপর একটু দম নিয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে বলল, দেন উ হ্যাভ টু ওয়াক, ওয়াক অ্যাণ্ড ওয়াক–বলেই থেমে গেল। মুখ নামিয়ে নিল।
ওরা আমার মুখে অসহায়তা দেখবে ভেবেছিল। কিন্তু এই দীর্ঘ পথ হাঁটার সম্ভাবনায় আমার চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠাতে ওরা আমাকে পাগল ঠাওরাল।
ধন্যবাদ জানিয়ে আমি সুইং-ডোর খুলে বেরিয়ে এলাম।
ওরা আমাকে শুভকামনা জানাল।
সন্ধে হয়ে আসছে। একটু আগে থেকেই টিপটিপ বৃষ্টি আর কনকনে হাওয়া। সঙ্গে ওয়াটারপ্রুফ ওভারকোট ছিল। ভাগ্যিস বাস থেকে নামার সময়ে সেটাকে সঙ্গে করে এনেছিলাম। অন্য কারণও ছিল। সকালে কেনা একটা ছোটো কনিয়াকের বোতল ছিল তার লম্বা পকেটে। তখন কি আর জানতাম যে হারিয়ে যাব? জানলে, ট্যাক্সি ভাড়ার জন্যে পয়সাটা রেখে দিতাম। এরপর আর কী? হাঁটা আরম্ভ হল। হন হন করে হাঁটি আর কোনো বড়ো মোড় এলেই থমকে দাঁড়াই। কোনো পথচারীকে শুধোই পার্দো মঁসিয়ে, তারপর আঙুল দেখিয়ে শুধোই এটাই কি সেভস্তেপোল বুলেভার্ড?
তারা হনহনিয়ে হেঁটে যেতে যেতে বলেন, উই উই। অর্থাৎ ইয়েস ইয়েস।
ঘণ্টাখানেক হাঁটার পর দুজন ষন্ডাগুণ্ডা লোককে আবার ওই প্রশ্ন করাতে তারা কাঁধ টান করে বলললে সরি! উই ডোন্ট স্পিক ফ্রেঞ্চ। উই আর অ্যামারিকানস। ট্যুরিস্টস।
শুনেই দাঁত বের করে বললাম, হাই! হাউ নাইস টু হ্যাভ মেট উ্য। ইংলিশ ইজ সাচ আ সুইট ল্যাঙ্গুয়েজ!
ওরা বলল, ইয়া ইট ইজ।
বলেই, পালিয়ে গেল।
হয়তো ভাবল, একটা-পাগল ন্যালাখ্যাপার পাল্লায় পড়েছে ওরা। অথবা ভিক্ষে-টিক্ষে চাইব হয়তো।
ঠাণ্ডায় আমার কান জমে ডিসেম্বরের শেষরাতে নেতারহাটের নেকড়ে বাঘের কান হয়ে গেল। ডান কান বাঁ-হাতে টেনে দেখলাম, সাড় নেই।
সাড় নেই। পথেরও শেষ নেই। শয়ে শয়ে লোক হেঁটে চলেছে। গাড়ি চলেছে লাইন দিয়ে। লাল সবুজ নীল হলুদ বাতি জ্বলছে নিভছে মোড়ে মোড়ে। এই লোক, গাড়ি, বাতি, পথ, কারও সঙ্গে কারও কোনোরকম কমিউনিকেশান নেই। আমার সঙ্গে নেই প্রাকৃতিক শীত ও ভাষার বিজাতীয়তার জন্যে। ওদের সঙ্গে নেই আন্তরিক শীত ও চরিত্রের জাতীয়তার জন্যে।
ব্যাপারটা আশ্চর্য কিন্তু সত্যি।
একটা মোড় পেরোবার সময় প্রায় একটা ছোটো ভক্সওয়াগেন বীটল গাড়ির নীচে চাপা পড়তে পড়তে একটুর জন্যে বেঁচে গেলাম।
খুব দুঃখ হল। চাপা পড়লাম না যে সেজন্যে নয়। চাপা পড়লে লজ্জার শেষ থাকত না। আমার দৃঢ়বিশ্বাস যে, গাড়ি যদি আদৌ চাপা পড়ে মরতে হয় তবে দোতলা বাস কি মালবাহী ট্রাক চাপা পড়ে মারা যাওয়া ভালো। পৈতৃক প্রাণটা দু-ক্ষেত্রেই নির্দ্বিধায় মৃদু টায়ার পাংচারের শব্দ করে বেরিয়ে যাবে কিন্তু লোকে তেমন ইম্প্রেসড হবে না প্রথম মৃত্যুতে। এমনকী এমনও মনে করতে পারে যে, আমার প্রাণটা বড়ো পলকা ছিল। ওইটুকু গাড়ি চাপা পড়ে মরল শেষে! কিন্তু বড়ো ট্রাক বা দোতলা বাসে চাপা পড়লে লোকের সমবেদনা অনেক বেশি হবে।
আমাদের কলেজের এক অল্পবিদ্যা-ভয়ংকরী অধ্যাপক লা ডলচে ভিটা দেখে এসে এই গাড়ি চাপার উপমা দিয়ে টু ডাই উইথ আ ব্যাং অ্যাণ্ড নট উইথ আ হুইমপারের সমীকরণ করেছিলেন।
এই হাঁটার কোনো মজা নেই–লোকজন দোকানপাট দেখার মজা ছাড়া অনেকের জীবনের চলার সঙ্গে এই হাঁটার খুব মিল দেখি। এটা একরকমের তুচ্ছ উদ্দেশ্যসম্পন্ন মুভমেন্ট। অ্যাকশান নয়। হেমিংওয়ে বলতেন–নেভার কনফিয়ুজ আ মুভমেন্ট উইথ অ্যান অ্যাকশান।
মুভমেন্টে গতি আছে কিন্তু প্রাণ নেই, কোনো মহৎ অথবা দুর্গম গন্তব্য নেই; সেটা অত্যন্ত আনইন্টারেস্টিং।
হাঁটতে হাঁটতে একসময়ে সেবাস্তেপোল বুলেভার্ডের সেই মোড়ে পৌঁছোব যে, সে তো জানা কথাই–কিন্তু পোঁছে কোনো রামাঞ্চ হবে না। পথের মধ্যে গতির মধ্যে গন্তব্যের মধ্যে রোমাঞ্চ না থাকলে পথটা, জীবনটা; বড়ো ভোঁতা হয়ে যায়।
শেষমেষ অনেক ট্র্যাফিক পুলিশ, অ্যানিমাল লাভারস-সোসাইটির সভ্য এবং আলিঙ্গনাবদ্ধ প্রেমিক-প্রেমিকাকে চমকে দিয়ে অত্যন্ত আনসেরিমোনিয়াসলি আমি আমার গন্তব্যে পোঁছোলাম।
পৌঁছে মনে হল, না পৌঁছোলেই ভালো হত। হাতে আড়াই ঘণ্টা সময়, পকেটে সামান্য পয়সা। পারফিউমের দোকানের মেয়ে দুটিকে যত গরিব আমি বলেছিলাম নিজেকে, সেই মুহূর্তে ঠিক তত গরিব ছিলাম না।
দেখলাম সামনেই একটি আণ্ডার গ্রাউণ্ড সিনেমা হল। কন্টিনুয়াস শো হয়। টিকিট কেটে ঢুকে পড়লেই হল। বড়ো ঠাণ্ডা মেরে গেছি। আপাতত একটা হিটেড ঘরে ঢুকে গা-গরম করা দরকার। বাইরে বেশ গা-গরম করা ছবি-টবিও ছিল।
ঢুকে পড়েই বুঝলাম যে, শুধু গা-গরমই নয় ওভারকোট এবং কোটেরও বোতাম খোল দরকার হবে এক্ষুনি।
এইসব সিনেমা, সাধারণত অপশ্চিমি দেশের লোকেরা এবং সেক্স সম্বন্ধে যেসব দেশ গোঁড়া ও যেসব দেশের পুরুষরা মেয়েদের এ সম্বন্ধে অনীহার কারণে সাধারণত সেক্স-স্টার্ভড –সেইসব দেশের লোকেরাই বাঁচিয়ে রাখে।
কিন্তু চুপি চুপি বলে রাখি, টিকিওয়ালা গোঁড়া মাতব্বরেরা যা-ই বলুন না কেন; এই সব ছবিকে আমাদের দেশীয় আণ্ডেকা রোশান হালুয়ার সঙ্গে তুলনা করা চলে।
আণ্ডেকা রোশান হালুয়া যদি আপনারা কেউ না খেয়ে থাকেন তাহলে কোনো আদি ও অকৃত্রিম হাকিমের কাছে গিয়ে আবদার করবেন। খুব কম হাকিমই অবশ্য এই পুরাকালের আশ্চর্য ঔষধির খবর রাখেন। বানানোর প্রক্রিয়াটা আমার জানা আছে। যাঁরা যৌবনেই বার্ধক্যে পৌঁছেছেন এবং গণ্ডারের শিংয়ের গুঁড়ো, ভাল্লুকের প্রত্যঙ্গ বিশেষের কাবাব, নানারকম বুজরুকি জরিবুটির খোঁজে বিস্তর মেহনতের টাকা বিলকুল পানিমে পানি করছেন তাঁরা যথাসাধ্য দক্ষিণা সহকারে আমার কাছে প্রার্থনা করলে আমি এর রেসিপি বাতলাতে পারি।
এ ওষুধটা বানানো সোজা, খাওয়া তার চেয়েও সোজা; কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই ওষুধ খাওয়ার পর এর গুণাগুণ পরীক্ষার পাত্ৰাভাব নিয়ে।
রসিক পাঠক আশা করি বুঝবেন কী বলতে চাইছি।
পাঠিকারা ক্ষমা করবেন।
অন্ধকার হলে ঢুকেই দেখি একটা দারুণ হ্যাণ্ডসাম ছেলে একটি নেভি-রু রঙা ফ্লেয়ার ও লাল-রঙা গেঞ্জি পরে (যেন ভারতীয় টেক্সটাইল মিলের বিজ্ঞাপন) সাইকেল চালিয়ে পাইন সুসের জঙ্গলের মধ্যের কাঁচা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে আর উলটোদিক থেকে পিংক-রঙা লেস বসানো ম্যাক্সি পরে মাথায় স্ত্র-হ্যাট চাপিয়ে একটি অপরূপ সুন্দরী মেয়ে লেডিজ সাইকেল চালিয়ে আসছে। কাছাকাছি হতেই কোনো দৈব-দুর্বিপাকে তাদের দুই সাইকেলে ধাক্কা লেগে গেল।
কে বলে হিন্দি সিনেমাই একমাত্র আজগুবি?
মেয়েটি পড়ে গেল, ছেলেটিও। মেয়েটির ম্যাক্সি অনেকখানি উঠে গেল। তার রাজহাঁসের শরীরের মতো কোমল ঊরুর একঝলক দেখা গেল।
তারপর তারা ফরাসি ভাষায় কীসব বলাবলি করল। আমি ভাবলাম গালাগালি করছে দুজন দুজনকে। ওম্মা! তারপরই দেখি সাইকেল দুটো মনমরা হয়ে পথের ধুলোয় জড়াজড়ি করে পড়ে রইল এবং সাইকেলের মালিক ও মালিকিনী রোদ-পিছলানো হলুদ জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গেল। তারপর দুজনে মিলে আঁচড়-কামড় দিতে লাগল দুজনকে।
আমি ভাবলাম ফরাসিরা খুব কালচারড জাত বলে বোধ হয় পথের মধ্যে মারামারি করাটা অভদ্রতা ভাবে। তাই জঙ্গলে গেল।
সেলুকাসের উচিত ছিল ভারতবর্ষে আসার আগে ফরাসি দেশে যাওয়া : তাহলে কী বিচিত্র দেশ : এই সার্টিফিকেট ফ্রান্সেরই প্রাপ্য ছিল।
এতক্ষণ হেঁটে যা ক্লান্ত হইনি তার চেয়ে অনেক বেশি ক্লান্ত হয়ে আমি বিস্ময়াবিষ্ট চোখে দেখতে লাগলাম সিনেমাতে সামান্য মানুষ ও মানুষীকে কী ঐশ্বরিক ও দীর্ঘস্থায়ী শক্তির অধিকারী করা যায়। কত সহজে কত কঠিন কঠিন শারীরিক যুদ্ধকে অবলীলায় ও কী নমনীয়তার সঙ্গে ইচ্ছেমতো প্রলম্বিত ও সুন্দর ও প্রায় নিরন্তর করা যায়।
এতদিন পরে হৃদয়ঙ্গম করলাম সিনেমাকে কেন মোস্ট এক্সপ্রেন্সিভ ফর্ম অফ আর্ট বলে।
তারপর বহুক্ষণ ধরে যেন পীপিং-হোলে চোখ রেখে আদম ইভ এবং তাদের সংখ্যাহীন কাজিনদের আপেল খাওয়ার পরের দুর্ঘটনা ঘটিয়ে যাওয়া দেখে যেতে লাগলাম।
মিথ্যে বলব না, খুব ভালো লাগছিল। আবার এ ছবির নায়কদের বড়ো ঈর্ষাও হচ্ছিল। বাংলা ছবির নায়করা শুধু পার্কের বেঞ্চে বসে মৃদু মৃদু ভাবে কথা কয়। তারা যদি এমন ছবির নায়ক হওয়ার সুযোগ একবারও পেত তাহলে হয়তো তাদের নায়কত্ব সার্থক হত।
আমার নিজের জন্যে, আমাদের দেশের নায়কদের জন্যে, দর্শকদের জন্যে খুব অনুকম্পা বোধ করলাম। টেক্সটাইল মিলের মালিকদের জন্যেও।
জামা কাপড়ের এমন হেনস্থা ক্রমাগত হতে থাকলে তো তাঁরা না খেয়ে মরবেন।
ঘড়ির রেডিয়ামে যখন দেখলাম সময় হয়েছে তখন নন্দনকাননের সমস্ত নন্দনতত্ত্বের মায়া কাটিয়ে উঠে পথে বেরিয়ে এসে যে রেস্তোরাঁতে আমাদের সঙ্গীরা এসে ডিনার খাবেন বলে ঠিক ছিল সেই রেস্তোরাঁর দিকে হেঁটে চললাম।
প্যারিসে একটা জিনিস দেখলাম যা অন্য কোথাওই দেখিনি। ফুটপাথের নীচে হাই-ড্রেনট এর মতো গরম হাওয়ার নর্দমা আছে। মাঝে মাঝেই ম্যানহোল কভারের মতো লোহার কভার বা জাল। তার ওপরে দাঁড়ালে নীচ দিয়ে গরম হাওয়া বেরোয় শোঁ শোঁ করে। শীতার্ত মানুষ ওখানে পঁড়িয়ে পা ও পশ্চাৎদেশ সেঁকে নিয়ে সুস্থ হয়।
পথে মাঝে মাঝেই একলা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পসারিণী। নানা বয়েসের; নানা রঙা চুলের। এই জগৎ সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। এদের সঙ্গে শোয়া-বসা না করলে নাকি কবি-সাহিত্যিক হওয়া যায় না। বড়ো বড়ো কবি-সাহিত্যিকদের কাছে ও তাঁদের লেখায় শুনেছি ও পড়েছি। অন্য ডিসকোয়ালিফিকেশান ছাড়াও এই এক ডিসকোয়ালিফিকেশানেই আমি হিটে ডিসকোয়ালিফায়েড হয়ে রয়েছি। এ জন্মে আমার বড়ো লেখক হবার কোনো চান্সই নেই।
পথ হাঁটি আমি, ময়লা মাড়াই, ধুলো ওড়াই, কথা কই; পথচারীর গায়ে গা লাগে। কিন্তু কোথায় যেন একটা বোধ আমাকে পীড়িত করে যে, আমি অন্য দশজনের মতো হাঁটতে পারি না। উড়তে পারি না সহজ পাখির মতো।
প্যাসিরের পথে দাঁড়িয়েই হয়তো ফরাসি কবি বোদলেয়ারের লেখা চারটি ছত্র তাই হঠাৎ মনে পড়ে যায়।
মনে পড়ে খুশি হলাম খুব।
চার্লস বোদলেয়ারের দ আলব্যাট্রস কবিতার লাইন কটি :
দ্য পোয়েট ইজ লাইক দিস মনার্ক অফ ক্লাউডস
ফ্যামিলিয়ার অফ স্টর্মস অফ স্টারস।
অ্যাণ্ড অফ অল হাই থিংগস
এক্সাইল্ড অন আর্থ এমিডস্ট ইটস হুটিং ক্রাউডস
হি ক্যানট ওয়াক বোর্ন ডাউন বাই
হিজ জায়ান্ট উইংস।
সেই আলোকিত রেস্তোরাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছি মিনিট পাঁচেক, তখনও টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে। এমন সময়ে জ্যাক-চালিত কসমস টু-টোয়েন্টির সেনট্রা বাসটিকে আসতে দেখা গেল।
আহা! যেন আমার হারানো প্রিয়া এল।
বাসভর্তি সহযাত্রীদের কাছে আমি যে এই দশ-এগারোদিনে এমন জনপ্রিয় হয়ে উঠেছি তা আগে বুঝতে পারিনি। এ জন্যেই গুণীরা বলেন বিচ্ছেদই ভালোবাসার গভীরতাকে উপলব্ধি করায়।
বাসসুদ্ধ লোক হুড়মুড় করে নেমে এল। বুড়িরা, যারা তাড়াতাড়ি নামতে পারলেন না তারা সিটে বসেই হাত নাড়তে লাগলেন।
সবচেয়ে প্রথমে এল জ্যাক। এসেই জড়িয়ে ধরে চুমু খেল। জ্যাক আজ সকালে দাড়ি কামায়নি। গাল জ্বলতে লাগল।
জ্বালা প্রশমিত হল ক্যারল, জেনি ও সারার চুমুতে।
বুড়িরা বৃষ্টিতে-ভেজা আমাকে দেড় বছরের ছেলের মতো ওই রাজপথে দাঁড়িয়ে ফণ্ডল করতে লাগলেন। ব্যাপারটা প্রথমে আনন্দের ও হাসির ছিল। কিন্তু আমার চোখ একটু পর ভিজে এল। ভগবানের কাছে বড়ো কৃতজ্ঞতা জানালাম। কত কী না তুমি দিলে! এই প্রবাসের সঙ্গীরা ও এই দু-দিনের পরিচয়ের মানুষগুলোর বুকে এত ভালোবাসা ও প্রীতি দিয়েছ তুমি! যা পয়সা দিয়ে পাওয়া যায় না, কাঙালপনা করে পাওয়া হয় না; সেই অমূল্য স্বার্থহীন অমলিন ভালোবাসা কত সহজে পেলাম। নিজের জন্যে, প্রত্যেক মানুষের জন্যে ভালোবাসায় ভাসমান আমার অন্তর এক কৃতজ্ঞ নম্রতায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।
যেই-ই এই আপাততুচ্ছ কিন্তু বড়ো দামি পাওয়া জীবনে পায়, কেবল সেই-ই জানে তার দাম।
ক্যারল ভেবেছিল আমি সীন নদীতে ডুবে মরেছি।
আমি বললাম, কোন দুঃখে? তাই যদি জন বলে তোমার কেউ না থাকত জানতাম।
ও হাসল, বলল, অসভ্য। হিংসুক! ভালোবাসা কি একজনকেই বাসা যায় জীবনে? আমাকে কি তুমি এতই সীমিত মনে করো নাকি?
বললাম, কী আছে আমার?
আমি জানি। তুমি নাই-ই বা জানলে।
জেনি বলল, অনেক ভাবিয়েছ এখন চলো একটু ফ্রেঞ্চ ওয়াইন খেয়ে আমাদের ধন্য করবে।
দলপতি জন, গোল্ড-ব্লক টোব্যাকোর টিনটা এগিয়ে দিয়ে বলল, হ্যাভ আ ফিল–তারপর বলল, হ্যাভ আ কাপল অফ স্টিফ কনিয়াকস। ঊ্য উইল বি অলরাইট।
ওয়াশরুমে গিয়ে বুঝলাম কেন জন অলরাইটের কথা বলল। একে তো যা কার্তিকের মতো চেহারা! তারপর বৃষ্টিতে ভিজে পাতলা চুলগুলো লেপ্টে গিয়ে একেবারে ঝোড়ো কাকের মতো অবস্থা হয়েছে। নাকটা লাল ও গাল দুটো বেগুনি হয়ে গেছে ঠাণ্ডায়। আশ্চর্য হলাম এই ভেবে যে একটু আগের সিনেমাতে ডজন ডজন অনাবৃত তরুণ-তরুণীর আদর করা দেখেও যথেষ্ট গরম হলাম না আমি? এ জন্মের মতো আমি কি ঠাণ্ডা মেরে গেছি?
খাদ্য ও সহসাথিদের প্রীতির সঙ্গে খাওয়ানো পানীয়তে শরীর চাঙ্গা ও উষ্ণ করে আমরা নাইট-টুরে বেরোলাম।
আজই প্যারিসে শেষরাত। আজ রাতদুপুর করে ফিরে কাল একটু বেলা করে বেরোব আমরা। তারপর লীল হয়ে বেলজিয়ামের অস্টেণ্ড। অস্টেণ্ড থেকে আবার বোটে ইংলিশ চ্যানেল পেরিয়ে ইংল্যাণ্ডের ডোভার। সেখান থেকে ভিক্টোরিয়া স্টেশান–লানডন।
রাতের প্যারিস, বাস বা গাড়ি থেকে দেখার নয়। হাতে প্রচুর সময় নিয়ে যেতে হয় সেখানে, মনটাকেও খোলামেলা সংস্কারশূন্য অবসরে ভরে নিতে হয়–তারপর পায়ে হেঁটে ঘুরতে হয়, থিয়েটারে, অপেরায়; নাইট-ক্লাবে।
এখানে রাতটাকেই দিন বলে মনে হয়, এত আলো, এত লোকজন, সারারাত সমস্ত দোকানপাট খোলা, রেস্তোরাঁ খোলা, কাফে খোলা; দেখলে ভাবতে হয় এরা দিনের বেলাতেই ঘুমোয় বোধহয় আমাদের দেশের গ্রাম-গঞ্জের স্টেশন মাস্টারমশাইদের মতো। রাতের বেলা মেল ট্রেন পাস করে বলে তাঁদের গভীর রাত অবধি জাগতে হয়, তাই দিনের বেলা পয়েন্টসম্যানের হাতে সবুজ নিশান, আর লোহার রাকেট দিয়ে দিনেই তাঁদের অবসর মেলে।
নিন্দুকেরা বলেন, গ্রামগঞ্জের মাস্টারমশায়দের স্ত্রী প্রায়ই দিনমানে গর্ভবতী হন।
তাই?
কিন্তু এখানে দিনও জাগে, রাতও জাগে; তাহলে এরা ঘুমোয় কখন?
আমাদের বাস এসে দাঁড়াল মূলারুজের সামনে। সেই চিত্রকর ভ্যানগগ থেকে সেজান সকলেই যে প্যারিস, যে মূলারুজে এসে বসতেন সেই মূলারুজে।
বাইরে উইণ্ডমিলের পাখার মত পাখা ঘুরছে। কলকাতার পার্ক স্ট্রিটের মূলারুজে এই মূলারুজেরই বড়ো করুণ অনুকরণ। সহজ সমীকরণ।
ঢুকতে হল লাইন দিয়ে। অ্যালাস্টার নিশ্চয়ই আমাদের টিকিটের বন্দোবস্ত আগে করে রেখেছিল, না কি করেনি জানি না, কিন্তু লাইন দিয়ে ঢুকলাম একথা মনে আছে।
বেশ ভালো জায়গায় আসন ছিল আমাদের। আসনে গিয়ে বসতেই শ্যাম্পেন দিয়ে গেল গ্লাসে। টিকিটের দামের সঙ্গেই এর দাম ধরা আছে। কেউ বেশি কিছু খেতে চাইলে বা অন্য কিছু খেলে পয়সা দিয়ে খেতে পারেন। কিন্তু স্টেজে একটু পরে যা দৃশ্য দৃশ্যমান হল তাতে কারও গ্লাসের দিকে চাওয়ারও অবকাশ হবে বলে মনে হল না।
প্রথমে শুরু হল বিখ্যাত প্যারিসিয়ান ক্যান ক্যান ডান্স। ক্যান ক্যান পরে সুন্দরীরা বাজনার সঙ্গে সঙ্গে ধেই-ধেই করে নাচতে লাগল।
এক একটা ক্যানক্যানে কত মিটার কাপড় লাগে তা-ই ভাবছিলাম। অথচ পৃথিবীতে মেয়েদের সমুদয় সাজপোশাকের আড়ম্বর শুধু খুলে ফেলারই জন্যে। ভাবলেই হাসি পায়। পুরষদেরই কারসাজি এসব। যা অতিসহজে দৃষ্টিগোচর করা যায়, বিনা আয়াসে সেই সুন্দর নারীশরীরটাকে বহু মিটার কাপড়ে মুড়ে তারপর কষ্ট করে খোলার কী প্রয়োজন জানি না। এও একরকমের বিকৃতি। তবে, ক্যান-ক্যান পরে মেয়েরা শুধু নাচেই, আদর খাওয়ার অব্যবহিত আগের পোশাক নিশ্চয়ই ক্যান-ক্যান নয়!
আমি বাঙাল মানুষ, আমার কাছে মেমসায়েব মাত্রই মেমসায়েব। চেহারা দেখে, কে আমেরিকান, কে ইংলিশ, কে জার্মান, কে ফ্রেঞ্চ, কে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান তা বলার মতো তালেবর আমি হইনি। এ জন্মে হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই। তবে, একটু-আধটু যে তফাত নেই, তা বলা যায় না। প্রত্যেক জাতেরই বৈশিষ্ট্য থাকে। চেহারায়, ব্যবহারে, চোখের চাউনিতে, ধন্যবাদ দেওয়ার মধ্যের উষ্ণতার তারতম্যে–এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।
ক্যান ক্যান নাচ শেষ হল যখন, তখন ম্যাজিক দেখানো আরম্ভ হল।
পশ্চিমের দেশগুলো বিজ্ঞানে অত্যন্ত উন্নত-তাই ম্যাজিক ব্যাপারটাকে ওরা একটা অন্য উচ্চতায় পর্যবসিত করতে পারত। ইচ্ছা করলেই। উত্তর পশ্চিম আমেরিকার পুরো ডিজনি ল্যাণ্ডটাই যেমন একটা ম্যাজিক। কিন্তু এই ম্যাজিকের বাবদে মনে হয় পশ্চিমিদের পুবের দেশের লোকের প্রতি একটা সহজাত সম্মান আছে। এমনকী হীনমন্যতাও আছে।
পৃথিবী বিখ্যাত মূলারুজ-এ যেমন ম্যাজিক দেখলাম তেমন ম্যাজিক আমার মেজোমামা গিরিডির মামাবাড়ির বারান্দায় পর্দা টাঙিয়েও দেখাতে পারতেন। আসলে, পরে বুঝলাম যে, এই ম্যাজিকটা স্টপ-গ্যাপ। ক্যান ক্যান পরা সুন্দরীরা যে কী ত্বরিৎগতিতে ড্রেসিংরুমে বিবসনা হচ্ছিলেন তার কোনো ধারণাই তখন আমার ছিল না। থাকা সম্ভবও ছিল না।
আমি যে দেশে জন্মেছি, বড়ো হয়েছি সেদেশে কোনো মহিলার গোড়ালির ওপরে কোনো দুর্ঘটনায় শাড়ি উঠে গেলেই পুরুষের বুকে স্পন্দন ও নারীর মুখে লজ্জা ফোটে। সেই দেশের লোক একটু পরে যা দেখলাম, তাতে বাকরোধ হয়ে গেল।
স্টেজের মধ্যে আরেকটা স্টেজ। কত টাকা যে খরচ করা হয়েছে এই স্টেজ বানাতে তার ইয়ত্তা নেই। এদের উচিত সত্যজিৎবাবুর স্কেচে ভর করে বংশী চন্দ্রগুপ্ত যে স্টেজ করেন তা দেখা। দেখে শেখা।
যাই-বোক, স্টেজে যখন একসঙ্গে প্রায় কুড়িটি তরুণী দৌড়ে এল, নাচল কুদল, সিঁড়ি দিয়ে উঠল নামল, যাতে আমরা পয়সা উশুল করতে পারি ভালো করে তখন ব্যাপারটা কী ঘটছে তা-ই ভালো করে বুঝতে পারলাম না।
ভগবানের উচিত ছিল মানুষকে দুটোর বেশি চোখ দেওয়া–এসব বিশেষ বিশেষ অকেশানে ব্যবহার করার জন্যে।
অতজন মেয়ে, তাদের কারও শরীরের কোথাওই কিছুমাত্র কাপড়-জামা নেই। তারা প্রত্যেকেই সুন্দরী, প্রত্যেকেরই দারুণ ফিগার, দারুণ নাক, দারুণ চিবুক; দারুণ বুক। কোথাওই কিছু নেই। কেবল একটুকরো গোলাকৃতি আধুলিসমান লাল, নীল, হলুদ, অথবা বেগুনে রঙিন রাংতা ছাড়া। সেই গোল করে কাটা রাংতাটুকু জায়গাবিশেষে কি দিয়ে জানি না সেঁটে রাখা হয়েছে। এত নাচা-কোঁদাতেও তা স্থানচ্যুত হচ্ছে না।
ফরাসি ক্রিমিনাল আইন বা অশ্লীলতার আইনে কী আছে জানি না, তবে রাংতার রক্ষণশীলতা দেখে মনে হল, ওদেশে আইনজ্ঞদের এবং আইন মান্যকারী ও অমান্যকারীদেরও যে বিলক্ষণ রসবোধ আছে একথাটা অস্বীকার করার উপায় নেই।
সম্পূর্ণ নগ্না সুন্দরীরা এল, গেল; কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়াল, ব্যালে করার অজুহাতে আমাদের দিকে হাত পা ছুঁড়ল। পেছন ফিরে দাঁড়াল, সামনে দাঁড়িয়েই ছিল, অনেক কিছুই করল যাতে কোনো নিমকহারাম দর্শক বলতে না পারেন যে, ওঁদের কাছ থেকে পয়সা নিয়ে ওঁদের ঠকানো হয়েছে।
অনেকে বলে থাকেন যে এই শো নাকি চমৎকার।
হয়তো চমৎকার! কিন্তু এই বাঙাল দর্শক, এই শোয়ে অংশগ্রহণকারী নগ্নতার চমৎকারিত্বে এতই অভিভূত, স্তব্ধ ও স্তম্ভিত হয়ে ছিল যে, শোয়ের চমৎকারিত্ব অবধি সে পৌঁছোতে পারেনি।
একসময়ে শো শেষ হল। সব শো-ই একসময়ে শেষ হয়। শেষ হয় যৌবন, জীবনও শেষ হয়। কিন্তু কীভাবে হয়, কোন উদ্দেশ্যে সেই সময়টুকু ব্যয়িত হয়; তার ওপর অনেক কিছু নির্ভর করে।
এই নগ্ন শো-এর চেয়ে আমার মায়ার খেলা অনেক ভালো লাগে। তার কারণ এই মূলারুজ-এর নাইট-ক্লাবের সমস্ত নিরাবরণ চমৎকারিত্ব শরীরে এসেই থেমে গেছে। মনের সঙ্গে এর কারবার নেই। এই শো চারঘণ্টা দেখার আনন্দের সঙ্গে তুলনা করে আশ মেটালে ফেরে না কেহ, আশ রাখিলে ফেরে এই একটি কলির সুর অনেক গভীরতর আনন্দের উৎস বলে মনে হয় আমার।
ইচ্ছে হল বলি, (ফারসি জানি যে বলব?) যে তোরা আমাদের দেশে আসিস। আমাদের দেশে কোনারক আছে, খাজুরাহো আছে কিন্তু তবুও আমাদের দেশের মেয়েরা কত শালীন, কত মিষ্টি করে তারা সাজে, কত সুন্দর করে হাসে, কত গভীর তাদের মনের প্রেমের দীপ্তি। তোদের নগ্ন স্টেজের, নগ্ন মেয়েদের সমস্ত উচ্ছলতা সেই একটি হাসির ঔজ্জ্বল্যরও সমকক্ষ নয়।
মনে মনে বললাম, আসিস ওদেশে।
মূলারুজে-এর আশার কাঁধ ঝুঁকিয়ে বলল, মেরুসী মঁসিয়ে।
যাঃ বাবা। ভেবেছে হয়তো আমি সুখ্যাতি করলাম শো-এর।
এইসব তরল শো-এর সব ভালো। মানে, যা এর ভালো। কিন্তু সবচেয়ে খারাপ যা, তা হচ্ছে এইরকম শো দেখে ফিরে এসে মাঝরাতে হোটেলের একা ঘরে শুয়ে থাকা!
ইচ্ছা করে, পরানডারে গামছা-আ-আ-দিয়া বান্ধি।
সরি, শরীলডারে।
আজ সকালে প্যারিসের হোটেলে ঘুম ভাঙল এক বিষণ্ণতার মধ্যে। বাইরে টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। দস্তা-রঙা আকাশ দেখা যাচ্ছে পর্দার ফাঁক দিয়ে। ঘরের মধ্যে ফিসফিস। ঘরের বাইরে ফিসফিস-কারা যেন শ্বাস ফেলছে অবিরল।
চোখ-মুখ ধুয়ে জামাকাপড় পরে তৈরি হয়ে নিলাম। তারপর স্যুটকেস হাতে নেমে এলাম নীচে ব্রেকফাস্টের জন্যে।
আজ রাতে লানডানে গিয়ে ডিনার খাব। ফুরিয়ে যাবে ইয়োরোপের ঘূর্ণিঝড়ের ছুটির দিন।
সকলেই একে একে বাসে এসে উঠলেন। জ্যাক আজ একটা হালকা নীল টুইলের শার্ট পরেছে, তার সঙ্গে গাঢ় নীল টাই।
অ্যালাস্টারের মতো বেশি লোক থাকলে কাপড়জামার ব্যাবসাদারেরা সব লালবাতি জ্বালাবে। গত পনেরো দিন সে তার কডুরয়ের ট্রাউজার, ছাই-রঙা উলের গলাবন্ধ একটি সোয়েটার এবং তার ওপরে একটি বাদামি কডুরয়ের কোট পরে দিব্যি চালিয়ে দিল। আণ্ডার গার্মেন্টস কী ছিল, স্বাভাবিক কারণে জানা ছিল না; তবে মনে পড়ে না ওর শার্টও কখনো দেখেছি বলে। নিশ্চয়ই প্রতিরাতে সেগুলো ধোওয়াধুয়ি করে নিত।
আমাদের দেশের মতো চান-টান করার উপায় নেই ওদের। বডিওড়োনাইজার বা শরীর সুগন্ধি আছে বহুরকমের। কী পুরুষ কী নারী সকলেই ফ্যাঁসসস করে সকাল-বিকেল বগলতলায়, ঘাড়ে গলায় একবার করে মেরে নিচ্ছে সুগন্ধি হাওয়া-ব্যস, তারপর সারাদিন ফুরফুর গন্ধ।
প্যারিসে ঢোকার সময়ে ওর্লি এয়ারপোর্ট দেখেছিলাম। পুরোনো এয়ার পোর্ট প্যারিসের। ফেরার সময়ে দেখলাম চার্লস দ্য গল এয়ারপোর্ট। এখনও পুরোপুরি চালু হয়নি সে এয়ারপোর্ট ওর্লির চেয়ে অনেক বড়ো।
কাল রাতে মূলারুজ-এ যাওয়ার আগে সাঁসে-লিজে গেছিলাম। এদিকে ছ-টা পথ, ওদিকে ছ-টা পথ। মাইলের পর মাইল সোজা। এদিকের থেকে আসা অগুন্তি ছয় সারির হেডলাইটের উজ্জ্বল আলো এবং অন্যদিকে যাওয়া টেললাইটের লাল আলোগুলি ভারি চমৎকার দেখতে লাগে।
মাঝ-সকালে কোথায় যেন একবার কফি-ব্রেক হল। নাম মনে নেই জায়গাটার। তারপর লীল হয়ে বেলা বারোটার আগেই অস্টেণ্ডে এসে পৌঁছোলাম–বেলজিয়ামে আবার। যেখানে বোট থেকে নেমেছিলাম।
ক্যারল ও জেনি বলল, চলো, আমরা একটু রোদে হেঁটে বেড়াই। সারাও দৌড়ে এল।
আমরা সকলেই জানি, আজ সন্ধ্যোবেলায় আমাদের সকলের সঙ্গে সকলের ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে। আজ থেকে বেশ কিছুদিন পর আমি ফিরে যাব আমার গরিব, নোংরা কিন্তু হৃদয়ের উষ্ণতার ওম ধরা কলকাতায়। ওরা ফিরে যাবে যার যার, বড়োলোক অথচ হৃদয়হীন দেশে। তারপর এ জীবনের মতো আর দেখা হবে না। কারও সঙ্গে কারোরই।
আমি জানি যে, ছাড়াছাড়ি হবার সময়ে বুড়ো জন আবারও বলবে, হ্যাভ আ ফিল, তার গোল্ড-ব্লক টোব্যাকোর টিনটা এগিয়ে দিয়ে; তারপর ওর বড়ো বোলের পাইপে একাট লম্বা টান দিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলবে–উই হ্যাড আ ওয়াণ্ডারফুল টাইম টুগেদার!
তারপর একটু থেমে বলবে, ডোন্ট উ থিঙ্ক সো?
আমি বিজ্ঞের মতো মাথা নাড়ব, বলব; ইয়া।
কিন্তু মনে মনে জানব, সমস্ত ওয়াণ্ডারফুল টাইমই একসময়ে শেষ হয়। আমরা কেউই শিখিনি, আমি, জন, ক্যারল, জেনি এবং অন্য অনেকেই; কী করে জীবনের প্রত্যেকটা মুহূর্তকেই ওয়াণ্ডারফুল করে তোলা যায়।
আশ্চর্য!
আজকের লাঞ্চটা বড়ো তড়িঘড়ির লাঞ্চ হল।
ইংলিস চ্যানেলে দাঁড়ানো জাহাজগুলো ভোঁ দিচ্ছে। বাঙাল যাত্রী আমি ইস্টিশানে স্টিম এঞ্জিনের কু–এবং নদীতে স্টিমারের ভোঁ শুনলেই মনে হয়েছে চিরদিন; আমার ট্রেন বা স্টিমারই বুঝি ছেড়ে গেল। এই ছেড়ে যাওয়ার ভয়টা ছোটোবেলা থেকে বুকের মধ্যে এমন করে সেঁধিয়ে ছিল যে, জীবনে যখন অনেক বড়ো বড়ো প্রাপ্তির ট্রেন ও স্টিমারও সত্যিই ছেড়ে চলে গেল আমায় তখন আর ভয় করল না।
একদিক দিয়ে ভালো। ভয়েতে অভ্যস্ত হয়ে গেলে আর ভয় করে না। তখন ভয় না করলে, ভয়ের কারণ না থাকলে; নার্ভাস-টেনসান হয়।
ক্যারল স্যুপ শেষ করে আমার চোখের দিকে ওর সুন্দর নীল চোখ মেলে বলল, উড উ্য রাইট টু মি?
আমি বললাম, সার্টেনলি ইয়েস।
তারপর একই স্বরে বলল, উইল উ্য কাম টু অস্ট্রেলিয়া?
বললাম, ওয়েল, মে বি। সাম ডে, সামটাইম। আই ডোন্নো।
ও বলল, ইফ ঊ্য এভার কাম, প্লিজ স্টে উইথ আস। তারপরই নিজেকে শুধরে বলল, আই মিন উইথ মি।
জেনি ফিক করে হেসে উঠল।
ক্যারল আস বলতেই, জেনি ভেবেছিল ক্যারল ওর জার্মান বয়ফ্রেণ্ডের কথা বলছে।
ক্যারল সত্যিই চটে গেল। বলল, স্টপ ইট জেনি।
আমি হাসলাম, বললাম, আমার সবচেয়ে বড়ো দুঃখ কী হবে জানো এই ট্রিপটা শেষ হয়ে গেলে?
কী? ওরা সমস্বরে শুধোল।
আমি বললাম, তোমাদের দুজনের সামনে বসে তোমাদের খুনসুটি দেখতে পাব না আর।
তক্ষুনি বুঝলাম। খুনসুটির ইংরেজি নেই। হয় না। যাহোক করে তাদের বোঝালাম।
খাওয়া-দাওয়া শেষ হল।
এবার জেটির দিকে যাবার পালা। বিকেলের রোদ ঝলমল করছে নানা-রঙা নৌকো ও জাহাজের গায়ে গায়ে। আজ কি ছুটির দিন? দিনের হিসাব হারিয়েছি। সব দিনই ছুটি। রোদের মধ্যেই একটা ছুটি ছুটি ভাব।
ওপরের নীল আকাশ, নীল ইংলিশ চ্যানেলের জলে মুখ দেখছে। সাদা সী-গাল ওড়াউড়ি করছে। আমরা যখন ডোভারে পৌঁছোব তখন প্রায় সন্ধে হয়ে আসবে।
লাইন দিয়ে একে একে আমরা জাহাজের দিকে এগোতে লাগলাম। আমার ফিলিপিনো সহযাত্রিনী একটা বড়ো চকোলেট দিয়ে বলল, মাই লাস্ট গিফট টু উ্য।
ভদ্রমহিলা বড়ো ভালো। সাধারণত অসুন্দর শরীরের মেয়েরা বড়ো সুন্দর মনের অধিকারিণী হন। ইনিও ব্যতিক্রম নন।
আমরা বোটে উঠলাম। তখনও লোক উঠছে। জেনি আমাকে দোতলার ডেকে নিয়ে গিয়ে এক কোনার একটা টেবিলে বসল। বসেই, ওর ব্যাগ খুলে সেই কাগজটা বের করল।
ওকে নিয়ে আমি ইংরিজিতে একটা কবিতা লিখেছিলাম, নাম দিয়েছিলাম ফর জেনি। কবিতাটি ওর খুব পছন্দ হয়েছিল–ক্যারলেরও। সারা বলেছিল, ট্র্যাশ। আমারও তাই ধারণা।
সেই কবিতাটির ওপরে জেনি একটা বলপেন বের করে আমার নাম ঠিকানা সব যত্ন করে লিখল, এমনকী আমার লানডানের ঠিকানাও, টরোন্টোর ঠিকানা, নিউইয়র্ক; লস-এঞ্জেলস এর ঠিকানা, এমনকী হনোলুলু এবং টোকিওর ঠিকানাও।
ও যখন সব ঠিকানাগুলো লিখছিল যত্ন করে, আমি বুঝতে পারছিলাম যে, লানডানের ভিক্টোরিয়া স্টেশনে নেমেই ও আমাকে ভুলে যাবে। ভুলে যাবে ক্যারল; সারা। ভুলে যাবে জন, জ্যাক; অ্যালাস্টারও।
আমিও ভুলে যাব ওদের। পথের আলাপ পথেই পড়ে থাকবে; পড়ে থাকে। বেশির ভাগ সময়েই। তার জের জীবনে, বাড়িতে; পথ-ছেড়ে-আসা মনে টানা যায় না।
টানা ভুলও হয়তো।
জাহাজ ভোঁ দিল। এত বড়ো জাহাজে নোঙর তোলার আওয়াজ শোনা যায় না। শুধু বিরাট বিরাট শক্তিশালী এঞ্জিনের একটা গোঙানির আওয়াজ। সেই চাপা গোঙানিটা জাহাজময় আমাদের সকলের মনে মনে ছড়িয়ে গেল। আমরা বেলজিয়ামের মাটি ছেড়ে এলাম। এখন মাঝ-সমুদ্রে। একদিকে রোদে-উজ্জ্বল অসটেণ্ড, অন্যদিকে নীল জল। সী-গাল উড়ছে। ঝাঁকে ঝাঁকে। আজ বড়ো শীত বাইরে।
আমার মনের মধ্যেও।