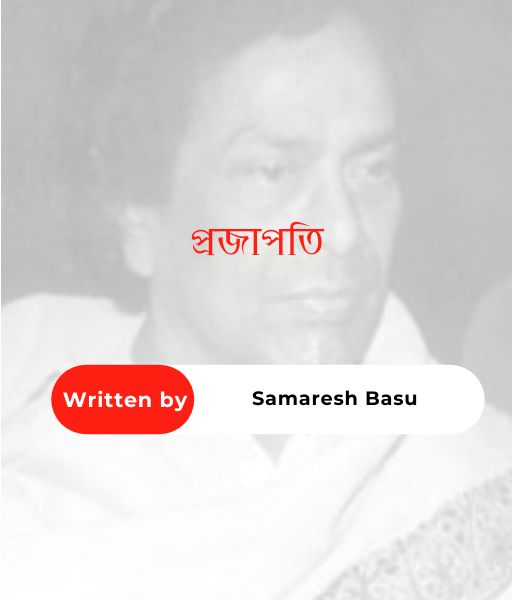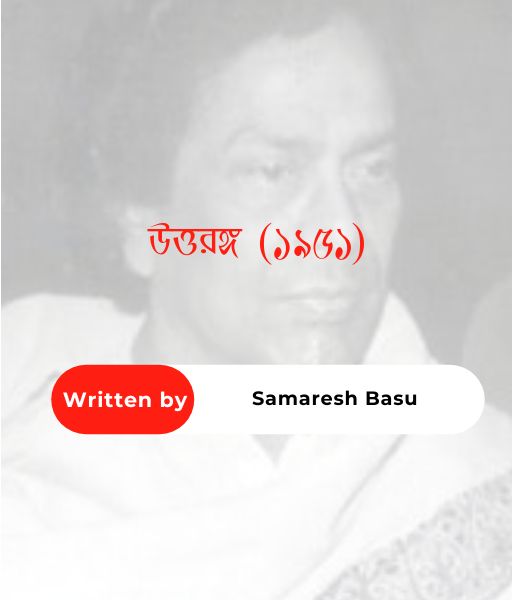০৬. পরদিন প্রভাতবেলা
পরদিন প্রভাতবেলা। তখনও সূর্য ওঠেনি। পূর্বাকাশে তার রক্তিম ইঙ্গিত দেখা দিয়েছে মাত্র। আর সমস্ত আকাশটা জুড়ে সাদা যাযাবর মেঘের দল উড়ে উড়ে চলেছে। ঋতু শরতের রূপ, আলো ছায়ার খেলায় বিচিত্র শরতের রূপ। ঘন সবুজে ভরা ঝাড় বন গাছের পাতাগুলো অল্প শিশিরে বোয়া নতুন কাজলে যেন চকচক করছে।
মাঠে মাঠে সবুজ শস্যের মেলা। মেলা নয়, ঋতু শরতের খাসা সবুজ ওড়নার লুটোপুটি মেলা। গোবিন্দ ঘুম থেকে উঠতেই প্রথমে তার মনে পড়ল মহিম গতকাল আসেনি। না আসার ব্যতিক্রমটা নতুন নয়, কিন্তু কারণ জানান দেওয়া থাকত আগে। আর ব্যতিক্রমটা এতই কম যে, সে কথা মনেই থাকে না। নিতান্ত অসুখ-বিসুখ না হলে শত ঝামেলা ঠেকিয়েও তো মহিম ক্ষণিকের জন্য দেখা দিয়ে গেছে। দু-দণ্ড বসবার সময় না থাকলে বলে গেছে, মনে বিঘ্ন নিয়ে চলে গেছে কথা বলতে না পারার জন্য। দৈনন্দিন জীবনের ব্যত্যয়টা এত বড়, ঘুম ভাঙতে মহেশ্বরের করুণা ভিক্ষার আগেই তো মনে পড়ল। মহিম কাল আসেনি।
বর্ষা শেষ, ম্যালেরিয়া জমে ওঠার সময়, সেই সঙ্গে আরও নানান রোগ। গোবিন্দ শঙ্কিত হল, মহিমের মঙ্গল কামনা করে মহেশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাল সে।
গোবিন্দ তরুণ। তার অধ্যাত্ম বিশ্বাস অজস্র দেবদেবীর ভারে আর ভিড়ে ঝামেলায় ঝালাপালা নয়। তার ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে মিশেছে জ্ঞানলাভের আকাঙক্ষা। যে অধ্যাত্ম জগৎ বিচিত্র এক রহস্যে ঘেরা, যা এ পৃথিবীর আড়ালে থেকেও নিয়মিত বিরাজমান, তার পরিচালক এবং পরিচালনার রহস্য সম্বন্ধে সে শিশুকাল থেকেই অনুসন্ধিৎসু।
এর কারণ আছে। তার বাবা ছিল তান্ত্রিক, তন্ত্রোপাসক। মহাশক্তির পূজারী। জীবনের শেষ কতগুলো বছর তার শ্মশানে মশানেই কেটেছে।
রাত্রিদিন ভাবে বিভোর, ধ্যানস্থ, সিন্দুরচৰ্চিত, সিন্দুরের মতো লাল চোখ ছিল তার বাবার। ঝড় বন্যা–কীট পশুর বিষ্ঠার আস্তাকুঁড়ে ছিল যাযাবর জীবনে। সাধনায় সে ছিল মহান গোবিন্দের কাছে। এ জগতে থেকেও ছিল না এ জগতে। জগৎ ছিল তার আলাদা। সাধারণের অদৃশ্যে সে—সেই জগতের মানুষের সঙ্গেই কথা বলেছে, খেলা করেছে। তাদেরই সঙ্গে জীবনের অবশিষ্টাংশ কাটাতে গিয়ে–ঘরের ভাত খায়নি কোনও দিন, স্পর্শ করেনি কোনও দিন এই ভিটে, মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অপরিহার্য কোনও বস্তু।
খেয়েছে মড়ার খুলিতে করে, মৃতের মেদ-মজ্জা-মাংস। মহাদেবের মতো প্রায় উলঙ্গ হয়ে যোগসাধনার জন্য পড়ে থেকেছে–নরকে। উজাড় করেছে পাত্রের পর পাত্র কারণ। চোখে না দেখলেও শুনেছে গোবিন্দ—এই সবই নাকি দেবপ্রাপ্তির আনুষ্ঠানিক কর্তব্যের খাতিরে। দেবত্ব প্রাপ্তি অর্থে শক্তিসাধনা একমাত্র কর্ম। সিদ্ধিলাভ অর্থে নিজের মধ্যেই সর্বভূতকে অনুভব করা। আরও শুনেছে, যা শুনে তার কিশোর হৃদয় প্রায় বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল আর কী, বিশেষ করে তখন অধজীবিতা তার মায়ের মুখের দিকে চেয়ে। তার মা তখন ক্রমাগত মোটা পাটের দড়ির গা থেকে এক এক পরত খুলে নেওয়ার মতো জীর্ণ ও ছিন্নমুখ হয়ে উঠেছিল। মুখে কিছু না বললেও, মায়ের এ ক্রমাগত অন্তিমের দিকে এগিয়ে যাওয়ার কারণটা প্রায় আঁচ করে নিয়েছিল সে। বোধ হয় সবই সয়েছিল তার মায়ের, সইল না, যখন শুনল তার প্রৌঢ় তান্ত্রিক স্বামী শ্মশানে ভৈরবী জাগিয়ে শিবত্ব লাভে তন্ত্রসায়রে নিমজ্জিত।
কিন্তু ধর্মবিশ্বাসী লোকেরা এ বিষয়ে টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করল না শুধু নয়, উপরন্তু মহাদেবের অংশ প্রাপ্তির এ মহান সাধনাকে প্রকাশ্যেই অভিনন্দন জানাল।
ভৈরবী? সে আবার কে? রাজপুরের চক্রবর্তীদের লুষ্ঠিতা ধর্ষিতা–সমাজের প্রান্ত থেকে বিতাড়িত এক আধা-রূপসী বউ।
কিন্তু তান্ত্রিকের স্পর্শে, সেই ধর্ষিতা পেয়েছিল সেদিন রক্তজবার অঞ্জলি ধার্মিক জনতার আকুল প্রসারিত হাত থেকে, যা নাকি গোবিন্দের মাকে নিঃসন্দেহে একেবারে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে। কিন্তু পিতার উপরে পুরোপুরি বিদ্রোহ করতেও কোথায় যেন তার একটা দ্বিধা ছিল। দুঃখটা মায়ের নিজের সৃষ্টি, প্রকাশ্যে না হোক, প্রকারান্তরে সে একথাই ধরে নিয়েছিল।
তারপর মৃত্যুর কয়েকদিন আগে তার মা তাকে সঙ্গে করে খালপারের শ্মশানে গিয়ে উঠল।
মহাদেবের মতো তখন তার বাবা হাড়গোড়ের মধ্যে আধশোয়া অবস্থায় শিব-নেত্রে বসে। অদূরে ছাইগাদায় অর্ধউলঙ্গ শায়িতা ভৈরবী। উভয়েই ভক্তবৃন্দ-পরিজনে ঘেরা।
সবই মনে হল গোবিন্দের বীভৎস। চোখ দুটো তার বুজেই গিয়েছিল ভয়ে, কিন্তু ভক্তিও কম ছিল না। এবং কারও নির্দেশ ব্যতীতই সে হাত তুলে দেবতাদের নমস্কার করেছিল।
ছেলের এই কাণ্ড দেখে, যেটুকু উৎসাহ আর আশা নিয়ে তার মা স্বামীর কাছে এসেছিল, তা যেন গেল আরও স্তিমিত হয়ে! ভয় পেয়েছিল পুত্রের মধ্যে এ ভত্তির সঞ্চারণ দেখে।
তবুও সে লজ্জার মাথা খেয়ে তার স্বামীকে ডাকল। আপত্তি না করে ভোলানাথভক্ত হেসে উঠে এল তার স্ত্রীর কাছে। সরে গেল তারা একটু আড়ালেএকটু দূরে।
সব কথা যেন মনে নেই গোবিন্দের। খালি মনে পড়ে তার মা ড়ুকরে উঠে যাবার পা জড়িয়ে ধরে ফেলে বলে উঠেছিল, মোরে খানিক চিকিচ্চে করিয়ে, মোর শরীলটারে ভাল করে তুললে না কেন? চিরকালই তো আর আমি এমনি কুৎসিত ছিলাম না। তোমার সঙ্গে শ্মশানে কেন, যে-কোনও নরকে গিয়েও তোমার ভৈরবী হইতাম।
গোবিন্দেরও বুকটা ফেটে যাচ্ছিল মায়ের ড়ুকরানিতে। কিন্তু সেদিন তার অতি অল্প রেখান্তিত গোঁফে ক্রোধও দেখা দিয়েছিল মায়ের এ ধর্মবিরুদ্ধ অবাচীনতায়।
কিন্তু আশ্চর্য! তার বাবা রাগ করেনি। কেমন এক রকম ভেঙে পড়ার মতো হেসে বলেছিল, এ কথা আজ আর কেন বলতে এলি ন বউ। ছোঁড়াটারে নিয়া ঘরে যা।
আর একটিও কথা না বলে চলে গিয়েছিল তার বাবা। তাকে নিয়ে ফিরে এসেছিল তার মা। কিন্তু কোথায় যেন মস্ত একটা ফাঁক থেকে গেল গোবিন্দের বুকে, যে ফাঁকটার মধ্য দিয়ে আজও হাহাকার শোনা যায়। যে হা হা শব্দ আজও তাকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে-অজানা নিরুদ্দেশ কোনএক পথে।
কয়েক দিন পরে মায়ের মৃত্যু সেই ফাঁকটাকে আরও বড় করে দিয়ে গেল, এল তার এক পিসিমা, তার রক্ষণাবেক্ষণের ভার নিয়ে।
কিন্তু গোবিন্দের জীবনের নীলাকাশে সেদিন এমনি শরৎ মেঘের ভিড়। কোথাও স্পষ্ট কোথাও দ্বিধা। কৈশোর জীবনটাকে এক অদ্ভুত গাম্ভীর্যে আর ছটফটানিতে ক্ষতবিক্ষত করে তুলল।
তাই আচমকাই সে একদিন শ্মশানে গিয়ে হাজির হল। ভৈরবী নেই, বাপ তার একলা। স্বস্তি পেল সে।
বাপও দেখল, কিশোর ছেলের কঠিন মুখ, জীবনের কোন এক আদিম নির্মম প্রশ্ন নিয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে। জিজ্ঞেস করল, বলল, বাবা, কী তোমার সাধনা?
বাপ বলল, সাধনা শক্তির, মহাশক্তির।
সে শক্তি কে, কোথায়?
সে সর্বভূতেষু। তাকে আপন ক্ষমতায় নিজের মধ্যে টানতে হয়।
তার কোনও আকার নাই?
আকার আমি নিজে, আমি আধার। আমিই সব। মহাশক্তির জন্য আমার সংগ্রামই সাধনা।
সে সংগ্রাম কী?
যমুনার উজান বইয়ে যাওয়া। মানুষের মন নিয়ত নীচের দিকে, তারে উঠতে হইবে উঁচু দিকে। ক্ষণজীবনের সব পরীক্ষায় তাকে পাশ করিতে হইবে। মানুষ নররূপে পশু, সে জন্য তাকে পাশবাচার করেই হজম করিতে হইবে পশুশক্তিকে। বিষপান করিয়াই মীলকণ্ঠ হইতে হইবে। তারপরেই বস্তু ও মানুষ ছাড়াই একলার মধ্যে সমস্ত আনন্দের অনুভব। তাই এখানে মন্ত্রের চেয়ে ক্রিয়া বেশি, ফিচার থেকে আচার প্রধান।
গোবিন্দ সব না বুঝলেও এটা বুঝল যে, বীভৎস হলেও এগুলোই সাধনগে। বলল, তবে তো তুমি সিদ্ধিলাভ করেছ?
শক্তি উপাসকের মুখ দিয়ে বিকৃত হয়ে উঠল। চোখ লাল। যেন এখুনি জল বেরুবে চোখ ফেটে। বলল চাপা স্বরে না, আমার সিদ্ধিলাভ হয় নাই।
তবে এসব?
এ-সবের সে উদ্দেশ্য করল, এ শ্মশন বাস, ভৈরবী, কারণ পান, মৃতদেহ ভক্ষণ ইত্যাদি। ক্ষণিক বিমূঢ় রইল তার বাবা, তারপরে আচমকা গর্জন করে উঠে ঝাপিয়ে পড়ল ছেলের উপর। এসব তোর মাথা হারামজাদা। বেরিয়ে যা এখান থেকে।
মার খেয়ে সরে গিয়ে গোবিন্দ বলল, আর এক কথা বলো। আমার মা কেন মরল?
আমি তাকে মেরে ফেলেছি।
বুকের সেই ফাঁকটা দিয়ে আর্তনাদ উঠল গোবিন্দের। বুঝল, ধর্মের নামে বাপ তার পাপ করেছে এবং শৈশবের বিচিত্র ধর্মবিশ্বাস থেকেই সে বুঝল, প্রায়শ্চিত্ত তাকেই করতে হবে। বলল, তুমি মরেও তো মার কাছেই যাবে। বলল, তোমাদের দুজনের সম্মতির সাধনা আমিই করব।
তান্ত্রিক কেঁদে উঠেছিল কি চেঁচিয়ে উঠেছিল, বোঝা যায়নি। বোঝা গিয়েছিল খালি তার কথা, জাহান্নামে যা,–
সেইদিন রাত্রেই সাপে ছুবলে মারল গোবিন্দের বাবাকে।
তাতেও খানিকটা শান্তি পেল গোবিন্দ, কিন্তু সে শান্তি এক অসহ্য বেদনাময়, বুকটা ভেঙে যাওয়ার মতো প্রায়। এর অন্য কোনও অর্থ গোবিন্দ করলেও আসলে এটা স্বজন-হারানোর শোক ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু এ হারানোর বিচিত্র রকমটাই রইল গাঁথা তার মনে।
ফলে এক অদ্ভুত দৃঢ়তার সঙ্গে সে আত্মনিবেদন করল মহেশ্বরের পদপ্রান্তে। বাপের উচ্ছলতার জন্যই বোধ হয় সে আশ্রয় করল ব্রহ্মচর্য। অধ্যাত্মবাদের সুর লয় তাল, ভক্তিতে শিহরণে, রহস্যাবৃত গাম্ভীর্য তাকে আচ্ছন্ন করল, তাকে টান দিল। যেমন টান পড়ে একতারার তারে, এক বিচিত্র সুরশব্দের সঙ্গে তার কাঁপে, কিন্তু স্থান বিচ্যুত হয় না। তা সে তুমি হৃদয় দিয়ে যে সুরই বাজাও, অনুক্ষণ বাজানোর ঝঙ্কার আর কম্পন সে যতক্ষণই থাকুক, একতারার কানে তো, সে বাঁধা। সুর এক সময়ে থামে, তার তখন অকম্পিত স্থির। গতিহীন। গোবিন্দ তাই সুরে আচ্ছন্ন বেপথুমান, কিন্তু বাঁধা রইল।
এবার দেখে শুনে কষে টঙ্কার দিল গোবিন্দের একতারাটায় রাজপুরের সাধক বিরাজ গোঁসাই। গোঁসাই তখন অলৌকিক সাধনায় গুরু ব্যক্তি, তার কালী কৃষ্ণ সমান, তার ধর্মালোচনা ব্যবহারিক জীবনেরও যোগসূত্র রক্ষা করে। তার ভাবে ও কর্মে সমন্বয় ঘটেছে, তাই ইহজগতে মন প্রাণ তার ইচ্ছাধীন। তার যেমন কম, তেমনি মন্ত্রও আছে। সে মন্ত্র দেয় লোককে। এ ধনজয়ীর সবচেয়ে বড় যা ছিল তা হচ্ছে মানুষের কাছে তার সাধক-স্বীকৃতি। গোবিন্দ তার শিষ্য কিন্তু বড় সংশয়াম্বিত, বিনা তর্কে বিশ্বাস নেই। তবুও গুরু।
একবারও ভেবে দেখেনি, ক্রমাগত টঙ্কারে সুরের তরঙ্গগুলো একের পর এক পেরিয়ে সপ্তমের ধাক্কায় তার না আবার ছিঁড়ে সুরভঙ্গ হয়। অবশ্য আজ পর্যন্ত সুরভঙ্গের লক্ষণ কিছু দেখা যায়নি। সুর এখনও আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধেই চলেছে।
ক্কচিৎ কখনও বাইরের ধাক্কা এসেছে, তবে সে ধাক্কা তারে আর সুরের চেয়ে—একতারাটার আত্মার উপরেই এসেছে বেশি, আত্মাটাকেই তার জন্য করতে চেয়েছে। এবং এখানেও সেই পাগলা গৌরাঙ্গের আবির্ভাব। ধাক্কাটা এসেছে তার কাছ থেকেই অত্যন্ত বিদ্বেষ আর বিক্ষোভের সঙ্গে। কিন্তু ধর্মের উচ্চ মান সেই আত্মা-জয়ীকে অবহেলাই করে এসেছে।
অধ্যাত্মবাদের প্রাচীন পুঁথিতে ঘরটা ঠাসা গোবিন্দের। দৈনন্দিন সেগুলো থেকে যা সে সঞ্চয় করে, তাই আলোচনা হয় তার সঙ্গে মহিমের। কিন্তু মহিম তো পাগলা গৌরাঙ্গের আনাড়ি অনভিজ্ঞ রূপ, তাই ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলে সে। গোবিন্দও এগিয়েছে, সে জবাব দেয় অদ্ভুত শান্তি আর ধৈর্যের সঙ্গে। নাস্তিকতাকে সে এক অদ্ভুত সৌম্য মিতার সঙ্গে, অবাধ্য শিশুর গালে চুমু খেয়ে শান্ত করার মতো ঠাণ্ডা করে দেয়।
মহিম শান্ত হয়, তৃপ্তি পায় না। ছেলে-ভুলানো চুম্বনে তৃপ্তি নেই তার। কিন্তু অশান্ত হয়েও উঠতে পারে না।
গোবিন্দ কাপড়ের খুঁটটা গায়ে জড়িয়ে ঘর থেকে বেরুল।
পিসিমা উঠোন নিকোচ্ছে আর প্রাত্যহিক বিড়বিড়ানিও শুরু হয়েছে। কান পেতে না শুনলে শোনা যায় না সে কথা।
ছেলে-মেয়ে নেই পিসিমার। নেই আর বিশেষ কোনও আত্মীয়স্বজন। চিরকাল তাকে খেটে খেটেই খেতে হয়েছে। ঘরে মাঠে গোয়ালেই তার জীবনটা প্রায় কেটে এসেছে, মাঝে এখানে আসার কিছুদিন আগে স্বামীর ভিটেয় থেকে গাঁয়ে শাকপাতা বিক্রি করেও কেটেছে। অভাবকে তাই সে বড় বেশি ভয় করে, ঘৃণা করে।
কিন্তু বিধি বুঝি বাম। চিরটাকাল দুঃখের সঙ্গে মোকাবিলা করে, যৌবনের ভরা বয়স থেকে বৈধব্য জীবন কাটিয়ে অভাবে অনটনের বিরাট ময়ালটার পাক থেকে যদিও বা পাওয়া গেল রেহাই—তাও বুঝি সইল না অনামুখখা দেবতার। পিসির কাছে দেবতা আজ অনামুখো কানা ছাড়া আর কিছু নয়। নইলে অমন ভাইপো নাকি তার বিবাগী বাউণ্ডুলে হয়। বাপ ছিল এক ধারার, ছেলে হল আর এক ধারার। বাপের ব্যাপার দেখেও’ ছেলের প্রত্যয় হল না। তাই আবার নতুন বিপর্যয়ের শঙ্কায় বৃদ্ধ বয়সেও শঙ্কিত হতে হয় পিসিকে। যদ্দিন বেঁচে আছে, সঙ্গে আছে পেট। এ বয়সে যদি আজ আবার নিশ্চিত গরাসটুকু খসে পড়ে, কোন্ আস্তাকুঁড়ে আবার ছিঁড়ে খাবে শকুনে।
চাষীর ঘর, কিন্তু গোবিন্দের বাপ ছেড়েছিল সে পথ। পথ ছাড়ার মূল্য হিসাবে জমিজমা বেহাত ততা কম হয়নি, কম হয়নি হারাতে।
অবশিষ্ট যেটুকু আছে, তাও বোধ হয় গোবিন্দই শেষ করবে। চাষবাস নেই, চাষীর ঘরের নেই সে জেল্লা, ধনে মানে ভরা সংসার। জমি রইল ভাগে দেওয়া, খোঁজখবর না নেওয়া আপদ বিশেষ। হায় ও আপদ না থাকলে কোথায় থাকত তোমাদের দুনিয়ায় বেহ্মজ্ঞান।
গোবিন্দকে দেখে পিসির বিড়বিড় করা থামল। উঠোন নিকোতে নিকোতেই বলল, হরেরামের কাছে একবার যেতে নাগবে আজ, সোমবচ্ছর সেই গোলমাল, আগে থাকতেই একটু হিসেব-নিকেশ করে রাখা ভাল বাপু।
হরেরামের কাছেই গোবিন্দদের জমি ভাগে দেওয়া আছে।
—আচ্ছা, আজ যাব। বলে গোবিন্দ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম করল।
–যাব টাব নয় বাপু। রোজই তো বলছিস যাবি। নয় তো ওকে ডেকে নিয়ে আয় মোর কাছে। আমিই সব জিজ্ঞাসাবাদ করে নিচ্ছি।
—তা যদি করো পিসি, বড় ভাল হয়।
পিসি জবাব না দিয়ে বিড়বিড় করতে লাগল।
গোবিন্দ বেরিয়ে গেল। তাদের বাড়ির পিছনের ডোবাটার ধার দিয়ে আখড়ার পিছনের ঘন কচুবনের পাশ দিয়ে যে স্যাঁতসেঁতে পথটা খানিকটা ঝোপেঝাড়ে ছওয়া অন্ধকারে এঁকেবেঁকে গেছে, সেটাই মহিমদের বাড়ি যাওয়ার সংক্ষিপ্ত পথ।
গোবিন্দ সেই পথেই চলল বন্ধু মহিমের সঙ্গে দেখা করতে। শরৎকালের এ সকাল বেলাটা–বিশেষ এই নির্জন ডাহুকের আস্তানার ধারে পথটিতে এক অনির্বচনীয় গম্ভীর আনন্দে প্রাণটা ভরে উঠতে চাইছে তার, কিন্তু মহিমের কথা মনে করে একটা বিশ্রী নীরব প্রশ্নে মথিত হয়ে উঠছে মনটা।
হঠাৎ মৃদু ঠুনঠুন শব্দে চমকে মুখটা তুলতেই বজ্রাঘাতের মতো নিশ্চল পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইল গোবিন্দ। যেন হঠাৎ চকিতের জন্য টাল খেয়ে উঠল তার সর্বশরীর। ব্যাপারটা তাকে এক রুদ্ধশ্বাস অস্থিরতা ও বিস্ময়ে (বিস্ময় কেন) আড়ষ্ট করে দিল।
দৃশ্যটা আখড়ার মেয়ে বনলতার কাপড় ছাড়ার দৃশ্য। ব্যাপারটা সত্যই বজ্রাঘাতের মতো কিছু নয়। আঁচলের শেষ প্রান্তটুকু তখন বুকের উপর দিয়ে টেনে দেওয়া ছিল বাকি। কিন্তু এ কচুবনে ডাহুকের নির্জন আস্তানায় সে তাড়া ছিল না বনলতার। ঘরের লোকজনের ভিড় কাটিয়ে তাই তো এসেছে সে কচুবনের ধারে, দিনের বেলাতে ও আধো-অন্ধকার ঝোপের ছায়াতে।
গোবিন্দকে বিস্মিত আড়ষ্ট করল কি তবে বনলতার উদ্ধত যৌবন। হ্যাঁ, বনলতা শ্যামাঙ্গিনী হলেও সুন্দরী। সাত বছরে তার প্রথম বিয়ে, আবার তেরো বছর বয়সে, তারপর উনিশ। কিন্তু তার জীবনের প্রজাপতির পাখা ঝাপটায় মৃত্যুই এসেছে বার বার, তিনবার তার তিনটি স্বামীকে ছিনিয়ে নিয়েছে। তবু ভেঙে পড়বার লক্ষণের বদলে, একুশ বছর বয়সে তার বলিষ্ঠ দেহে বিদ্রোহের ছাপটাই চোখে পড়ে। পড়ে বোধ হয় একটু বেশি করে।
মুহূর্ত মাত্র। গোবিন্দ বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো ফিরে গেল। সে মেনে নিতে চাইল না তার যৌবনের এ বিপর্যয়কে, অনিচ্ছাকৃত আচমকা একটা বিরক্তিকর দৃশ্য ছাড়া। একমেবাদ্বিতীয়মের এ সাধকটি তার সৌন্দর্যপিপাসু সুন্দর চোখ দুটোকে মনে মনে খুব কষে খোঁচাল। মনে মনে বলল, জীবনের বিয়গুলোর এটা একটা।
কিন্তু চোখ এড়াতে পারল না বনলতার। চকিতে কাপড়টা টেনে দিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠল সে। ডাকল, সাধু, সাধু, শোনো!
গোবিন্দকে সে বলে সাধু। প্রতিবেশী হিসাবে, গোবিন্দের কাছে তার প্রগলভতার বাড়াবাড়ি লোকচক্ষুর আড়ালে নয়। বিদ্রোহের যত প্রকাশ তা এই শান্ত সাধকটির কাছেই তার বেশি। সে ভাবাসে শান্ত সাধকটির নিরবচ্ছিন্ন সাধনায় বাধা দিতে। তার সাধনাকে ভীরু বলতে। সে ভালবাসে সাধকটিকে বিরক্ত করতে, মনোকষ্ট দিতে, জ্বালাতন করতে, কঠিন বিদ্রূপে আঘাত করতে। এমন কী, পিসির হয়ে কোমর বেঁধে গোবিন্দের সঙ্গে ঝগড়া করতেও দেখা যায় তাকে। পিসির সঙ্গে গলা বাড়িয়ে অনুযোগ করে, ধর্ম-উদাসী বাউণ্ডুলেগিরির জন্য। কত রূঢ় কথাই তাকে বলেছে গোবিন্দ, সবই ধুয়ে গেছে যেন জলতরঙ্গে, অত মান-অপমানের ধারে ধারে না বনলতা।
বনলতার ডাকে গোবিন্দ দাঁড়াল, কিন্তু ফিরে তাকাল না।
মুখ টিপে হাসল বনলতা। বলল, কাছে এসো।
বল না, কী বলবি? গোবিন্দ দূর থেকে বলল।
অত চেঁচাতে পারব না, কাছে এসো।
মোর সময় নেই।
ওঃ, কী একেবারে মাঠে তুমি পাকা ধান ফেলে আসছ!
ঠাট্টা হলেও কথাটার মধ্যে একটা পারিবারিক খোঁচা ছিল, যে কথা বলার অধিকার বনলতার নেই বা তাকে কেউ দেয়নি। তবে তাকে দেওয়ার দরকার হয় না, অধিকার সে নিজেই নিতে পারে। কেন না, গোবিন্দর কাজ সংসারের কাজ নয়, মানুষের দৈনন্দিন ছোঁয়াচ তার নেই বললেই হয়। তার কাজ, তারই কাজ, আর কারও নয়।
বনলতা নিজেই কাছে এসে দাঁড়াল। বেশ বোঝা গেল, রুদ্ধ দুষ্টামিতে তার চোখ দুটো কী অদ্ভুত খেলায় নাচছে। বলল, বলছি, তুমি যেন সাপ দেখে চমকে উঠল।
সাধকের মনে খানিকটা ঘৃণাবোধই হল। জেনে শুনে নিজের গোপনতম লজ্জার কথা প্রকাশ করতে কুণ্ঠিত তো হলই না এ বৈরাগীর মেয়েটি, উপরন্তু সেই লজ্জার কথাকে নিয়ে দুর্নিবার কৌতুকে হাসছে। তবুও কথাটা নেহাত খারাপ বলেনি বনলতা, তাতে মনের তার যে ভাবই প্রকাশ পেয়ে থাক। কেন না, সাপের মতো কুটিল হীন পরিহার্য দৃশ্য ছাড়া সেটা সত্যই তার কাছে আর কিছু নয়।
গম্ভীর হয়ে বলল সে, সাপের চেয়েও বুঝি খারাপ। কিন্তু তোর কি লজ্জা নেই বনলতা?
—তোমার কাছে? চকিতের জন্য যেন সমস্ত হাসি-মস্করা কাটিয়ে বনলতা অভূত গাভীর্যে থমথমিয়ে উঠল। পর মুহূর্তেই হেসে বলল, নাই আবার! এত লজ্জা যে মোর রাবার ঠাঁই নাই গো সাধু–
বাক্পটীয়সী দাবী বৈষ্ণবী, লজ্জা না থাকার বাহাদুরিতে যেন ফেটে পড়ছে বলে মনে হল গোবিন্দের। বলল, তবে?
—তবে আবার কী? কোথাও মোর ঠাঁই নাই বলেই সে ঠাঁই রাখি তোমার কাছে।
আশ্চর্য অসতীর কথাই বটে। এমন স্পষ্ট দুর্নীতির কথায় মনটার কোণে কালি লাগল গোবিন্দের। সে চাইল না আর এ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে। এর পরের কথার প্রসঙ্গ যে কীভাবে টানবে বনলতা, তা আন্দাজ করে কোনও কথা আর সে বলল, ফিরে চলল। বনলতা মুখে কাপড় চেপে হাসল। তারপর বলল, সাধু, তুমি মহিমের ঠাঁই যাবে।
-কেন?
–যাও তো তারে বলল, আমি ডাকছি। কাল তো সে আসে নাই। আর আবার সে গোবিন্দের কাছে এসে দাঁড়াল। বলল, যে পথে যাচ্ছিলে, সে পথেই যাও। কালনাগিনী সরে গেছে।
এবার হেসে উঠতে গিয়ে যেন খট করে বাজল বনলতার। কালনাগিনী। সেকথা বনলতা নিজে বলবে কেন, সবাই বলে। কালনাগিনী বনলতা, অনেক খেয়েছে অনেক দুবলেছে, কালনাগিনীর নিশ্বাসের বজ্র-ভয় কার নেই। কালনাগিনী বনলতা, ফণিনী মাথায় মণি ধরে বিচিত্র রূপবতী, কিন্তু কী সাংঘাতিক, গাঢ় নীল বিষে অনুক্ষণ মৃত্যু বয়ে বেড়ায়। তার রূপ-যৌবন–সই বিষ, নিবাসে বিষ! তার রূপের নীরব টান, উগ্র লোভাতুর করে, নয়নপুরের কত উষ্ণ বুকে দমকা নিখাস ভারী হয়ে ওঠে, কিন্তু ত্রাস। ভয়, প্রাণের ভয়, কালনাগিনীর নিশ্বাসের ভয়।
কিন্তু গোবিন্দ তটস্থ হল বনলতার কম্পিত ঠোঁটের দিকে তাকিয়ে। ছলের তো অভাব নেই বনলতার। এই হাসি, এই কান্না, আবার কোনও নতুন পরিস্থিতি তৈরি করার ফিকির করছে হয় তো। তবু নিষ্ঠুর সাধকের মনের কোণে হাতের তালুতে মোটা চামড়ায় ছোট্ট বেত কাটা সামান্য বেঁধার মতো একটু লাগল—আচমকা বনলতার ঠোঁট কাঁপানিতে আর চোখের কোণে উগত জল দেখে।
আর কোনও কথা না বলে সে কচুবনের ভিতর দিয়েই চলে গেল।
গেল না বনলতা। কাপড়ের আঁচলটা সজোরে মুখে চেপে কামায় সে ভেঙে পড়ল। কেন? কেন কান্না? কেন এমন করে কাঁদতে হয়? কান্নার বেগ যে বুকফাটা। কেন এ অসহ্য কারা?
কেন, এ প্রশ্ন বুঝি বনলতারও। তাই অস্ফুট আর্তনাদে এ ডাহুকের আস্তানা মথিত হয়ে উঠল, কেন, কেন, কেন? হৃদয়ের অন্ধ বদ্ধকারাকক্ষের দেয়ালটাকে আঁচড়ে ক্ষতবিক্ষত করে চোখের জলে ড়ুবে গেল বনলতা। তার চেঁচিয়ে বলতে ইচ্ছা করল, ভগবান, আমার এই বুকটাকে ছেঁচে-কুটে ধ্বংস করে দাও, আমাকে মুক্ত করো।
হঠাৎ পিঠে একটি আলতো স্পর্শে চমকে উঠল বনলতা। তাকিয়ে দেখল বৈরাগী নরহরি। লম্বা রোগা সুগায়ক নরহরি, বনলতার বাবার পালিত পুত্র-বিশেষ। গানই তার পেশা। অধুনয়নপুর নয়, নয়নপুরের ওপার রাজপুর থেকে শুরু করে বহু দূর বিস্তৃত অঞ্চলে নরহরি পরিচিত। উদাসী, সাতে পাঁচে না-থাকা নরহরি সকলেরই প্রিয়পাত্র। এমন কী পাগলা গৌরাঙ্গেরও।
বনলতা তার বান্ধবী।
–কাঁদো কেন সই? নরহরি জিজ্ঞেস করল।
কেন কাঁদে বনলতা? নরহরির এ স্নেহ-প্রশ্নে কান্না যেন বেড়ে উঠতে চাইল।
মনে পড়ল নরহরির, গোবিন্দ গেল এই কিছুক্ষণ আগেই, বনলতাকে বুঝি দুঃখ দিয়ে গেছে সেই পাষণ্ড সাধক।
বলল, সই, জগৎ, আর মানুষ, সবই বুঝি মাটির প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে লাগে তাতে। কেঁদো না, ঘরে যাও। মানুষের জীবনের সাধনা নাই নাকি? আছে, সাধনা আছে কেঁদে তো লাভ নাই।
ও, নরহরি বুঝি বনলতার অন্ধ বদ্ধ কারাকক্ষের সেই বন্দিনীটিকে চেনে, তার আত্মার পথচলার অলিগলিগুলোর নীরব দর্শক।
বোধ হয় শান্তি পেল বনলতা; লজ্জাও পেল বোধ হয় একটু এ নির্জন ডাহুকের আস্তানায় কালা ধরা পড়ে। তবু নরহরিই তো মনের কথা অকপটে খুলে বলার একমাত্র মানুষ তার। যা বলতে পারে না, তা নরহরি পুরুষ বলে। কিন্তু নরহরিকে তা বলতে হয় না।
নরহরির কথার জবাবে বলল চোখ মুছে বনলতা, জীবনটার ভার আর সইতে পারি না, পরানটার যেন দাম নাই আর।
–ছি সই, ওকথা কয়ো না। যুগ যুগ ধরে অজগরের মাথায় যে মণি গজায়, তা যে দেখে সে রাজা হয়। ক’জনা তা দেখতে পায় কও! যেদিন দেখবে, সেই আলোয় নিজেরে চিনবে রাজা। পরানের দাম নাই তোমার? তোমার পরান তুমি দেখালে কারে, আর দেখলেই বা কে? যাও, ঘরে যাও।
বনলতা সামলে উঠল অনেকটা। হেসে বলল, কথা তুমি খুব কইতে পারো গোঁসাই। বলে কচুবনের মধ্যে দিয়ে আখড়ায় দিকে চলল সে।
সেদিকে তাকিয়ে নরহরি হাসল। তার বলিষ্ঠ ঘাড় নুয়ে এল। গুনগুন করে উঠল সে, ভনয়ে বিদ্যাপতি-কৈছে নিরবহ, সো হরি বিনু ইহ রাতিয়া।
বার বার করে পদটি গাইল সে। তার সেই গুনগুনানি কাপড়ের আঁচল আটকা-পড়া মৌমাছিটির মতো বনলতার সঙ্গে আখড়া পর্যন্ত গেল। সেও গুনগুন করে উঠল : ‘সো হরি বিনু ইহ রাতিয়া।’