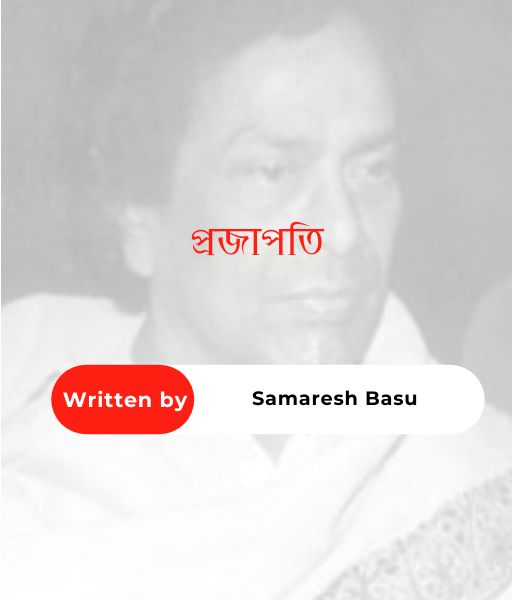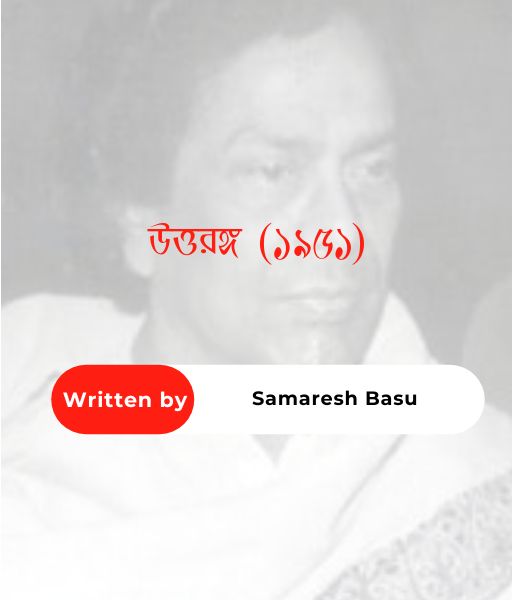১৮. কোজাগরী লক্ষ্মীপূর্ণিমার দিন
কোজাগরী লক্ষ্মীপূর্ণিমার দিন বিকালবেলা গোবিন্দ আচায্যির বাড়ি থেকে রাজপুরে ফিরছিল। এখনও সে তেমনি আত্মহারা, যন্ত্রণার ছাপ সুস্পষ্ট মুখে। যে জগৎ তার কাছে বেতাল লেগেছে তার তালই যে শুধু আজ পর্যন্ত পায়নি, তা নয়। সমস্ত বেতালটা আজ তার মস্তিষ্কে অগুনতি হাতুড়ি পেটানোর মতো পিটিয়ে চলেছে। পাগলা বামুনের সঙ্গে তার নিত্য কথা বাদ-প্রতিবাদ জানাজানি চলেছে। ভগবান নেই বা না-মানার স্বপক্ষে নয়, বাস্তব জগৎ সম্পর্কেই লক্ষ কথা। শেষটায় পাগলা বামুন তাকে স্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছে, গোবিন্দ বিনাশ্রমে ফাঁকি দিয়ে খায়। সে ধর্ম নিয়ে থাকুক, ভগবানকে পাওয়ার জন্য যাক যেথায় খুশি, কিন্তু সংসারের হাড়কালিকরা মানুষের শ্রমের খাবারে সে কেন উদরপূর্তি করবে? মানুষের সবটাই হাতেনাতে। সে তার মগজে আর শরীরে খাটে, তাই সে খায়। তার কাজের শেষ নেই। কিন্তু গোবিন্দ। বুঝলাম, হয়তো সে মানুষের চিত্তশুদ্ধির দায়িত্ব নিতে চায়, কিন্তু তা ধর্মের নামে কেন? দেশবাসী নিরক্ষর, ক্ষুধার্ত। ধর্ম দিয়ে কি তা ভরাট হবে? ঘরে বাইরে কেবলি কলহ, বিবাদ, হানাহানি মারামারি, ঘৃণা আর নীচতা। তার মূল তো ধর্ম নয়, তার অভাব, তার সমাজব্যবস্থা। যার পায়ের তলায় মাটি নেই, ধর্ম তার মাথায় কি ফুল ফোটাবে আপসে! সে যুক্তি এমনই নিচ্ছিদ্র, বিভ্রান্ত গোবিন্দের মুখে একটা কথা জোগায়নি। আরও বলেছে গোবিন্দর চিরকাল ব্রহ্মচর্য অবলম্বনের সম্পর্কে যে, এটা হল রাজপুরের আচায্যির নিজস্ব কার্যসিদ্ধির স্বার্থের জন্যই। আচায্যি সেই পুরনো ধর্মের দোহাই তুলে তার প্রচার এবং নিজের আচায্যিপনাকে জাহির করবার জন্যই তার দরকার গুটিকয়েক নির্বিকার অবিবাহিত সংসারে কোনও কিছুতে-না-মজা কিছু যুবককে। আচার্যের বিবাহ তো দোষের হয়নি। তারপর আচায্যির ধর্মের আন্দোলনের যে মূলটা, সেটা কি দক্ষিণভারতে ইসলামের অনুপ্রবেশ ও উত্থানের মুখে শঙ্করাচার্যের উদার ধর্মবিপ্লব এবং চৈতন্যের জাতিহীন ধর্ম আন্দোলনের সম্পর্কে গভীর আলোচনা এবং ভারতীয় সমাজের এই বিংশ শতাব্দীর প্রায় অর্ধেকের মুখের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে পাগলাবামুন স্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছে। যে, আজকের আচায্যির এ আন্দোলনের উৎস মঙ্গলজনক তো নয়ই, ধর্মের তীব্র হলাহলে জাতির আত্মহারানোর পথ। কী মূল্য আছে আজ মসজিদের আদর্শে কতকগুলো একেশ্বরবাদীর জনাগার খুলে। আচার্য বলেছে তার কালী কৃষ্ণ এক, তার মন্দিরে কোনও মূর্তি নেই। বলে, নিজের মনের দিকে তাকাও। ভাল। কিন্তু মন্দির কেন? কেন অলৌকিকতাবাদ? কেন পেশা আর পয়সা। একটা সময় গেছে যখন হিন্দু ভদ্ৰপরিবার সমাজের নিষ্পেষণ সইতে না পেরে ব্রাহ্ম হয়েছেন, বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন ব্রাহ্মণ্য ধর্মনীতির বিরুদ্ধে। কিন্তু আজকের মানবসমাজকে এক ইঞ্চি এগিয়ে দেওয়ার আকাঙক্ষাও যে মানুষের আছে, ধর্মের দোহাই তুলে তা নিতান্তই অসম্ভব। একে বলে খোদার উপর খোদৃগিরি করা। মানলাম, ভগবানই যদি তোমাকে গড়ে থাকে, তবে গড়েছে তো মানুষ করে? তবে মানুষের মতো মানুষ না ব কেন? আমি করব আমার কাজ, অনাচার বাদ দিয়ে। বাঁচার পথে আছে অত্যাচার, অবিচার, ‘আমি রুখব তাকে। তাতে যদি মরি, সে তো সবার বড় মরণ। যে আগুন লাগায়, আমি তাকে পরাস্ত করে নেভাব আগুন। সে-ই তো বলি তবে সেবা। ভগবান যদি মঙ্গলময়, তবে এ-ই তার নির্দেশ নয় কি? নাকি আমাকে টানতে যেতে হবে তারই দোয়ার? কেন রে বাপু?
হ্যাঁ, স্তব্ধ নির্বাক থাকতে হয়েছে গোবিন্দকে। কেবলি ছুটে ছুটে গেছে আচায্যির কাছে। যুক্তি দাও, যুক্তি দাও। কিন্তু সেখানে যুক্তি নেই, কেবলি বিশ্বাস, অন্ধ বিশ্বাস। অন্তরে দুবার ঝড় নিয়ে তবু গোবিন্দ আচায্যির ভজনাগারে বসছে, ধর্মসভায় যাচ্ছে, প্রচারে যাচ্ছে গ্রাম হতে গ্রামান্তরে। কিন্তু সেই তেজ আবেগ বিশ্বাস কই!
আর এ চিন্তারই গাঁটে গাঁটে মিশে আছে বনলতার মুখ, বনলতার কথা। এরই ফাঁকে ফাঁকে চমক লেগেছে বনলতার এক একটি তীব্রকথায়। বামুনের কথা জ্ঞানের মহিমায় গভীর, মার্জিত। বনলতার জীবনে ধ্যানের ভাষা অমার্জিত কিন্তু মূলত এক। সে হল, জীবনকে ছিনিয়ে নিতে হবে সব বাধা থেকে, প্রাণভরে বাঁচতে হবে। আর নিজেকে সে কেমন করে চোখ ঠারবে যে, বনলতার বলিষ্ঠ জীবন-আকাঙক্ষা ও উদ্ধত যৌবনের কাছে কেবলি তাকে মাথা নত করে পালিয়ে আসতে হয়েছে, কখনওই বুক টান করে দাঁড়াতে পারেনি। অথচ শৈশবে মহিমের সঙ্গে তার বনলতাকে নিয়ে যে বউ দাবির বিবাদ হয়েছে, সে কথা মনে করে তার বুকের মধ্যে যে রঙ্গরসের জোয়ার, তা কি স্তব্ধ হয়ে গেছে? হায়, বনলতার অপলক চোখ আজ তার মতো পুরুষকে পীড়ন করে। সে কি পলায়মান, সে কি কাপুরুষ বলে!
এমনি গোবিন্দের জীবনে চিন্তায় ধারণায় এক তুমুল আবর্তের সৃষ্টি হয়েছে। সেই আবর্ত ঠেলে উঠতে গিয়ে প্রাণ তার ওষ্ঠাগত। অথচ মানুষ বলেই এ অবস্থায় নিশ্চিন্ত থাকাও চলে না।
এসব ভাবতে ভাবতেই খালের খেয়াঘাটে এসে দাঁড়াল নয়নপুরে যাবে বলে। সূর্য অস্ত যায়, পশ্চিম আকাশ লালে ধূসরে গোধূলির লীলাক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। পুবে এর মধ্যেই মস্ত বড় চাঁদখানি উঁকি মারছে। দিনটির ঝলমলে বাহার দেখে কাকপক্ষীর এখনও ঘরে ফেরার কোনও তাড়া নেই যেন। আজ লক্ষ্মীপুজো ঘরে ঘরে, সাড়া পড়েছে তার। নৌকা তখন ওপার ঘাটে যাত্রী নিচ্ছে।
ঘাটে খেয়াযাত্রী মাত্র একটি মেয়েমানুষ নয়নপুরে যাবার। গোবিন্দকে দেখেই মেয়েমানুষটি মস্ত একটি ঘোমটা টেনে দিয়ে সরে গেল। কিন্তু চকিতে সে মুখ দেখে চমকে উঠল গোবিন্দ। তার শৈশবের স্মৃতিপটে ও মুখ আঁকা আছে, তা তো ভোলবার নয়! এক দারুণ উত্তেজনা তাকে পেয়ে বসল। সে বলল, ঠাকরুন কোথায় যাবে তুমি?
ঘোমটার আড়াল থেকে জবাব এল, নয়নপুর হাটের ধারে, মালীপাড়ায়।
কুণ্ঠায় মনটা দেবে গেল গোবিন্দের। মালীপাড়া যে খারাপ মেয়েমানুষের পাড়া! তবু বলল, রাজপুরের চক্কোত্তিদের ভাদ্দর বউরে চেনো তুমি?
এক মুহূর্ত নিস্তব্ধ। জবাব এল, চিনি।
তুমি কি ঠাকরুন সেই বউ?
ক্ষণিক নিশ্চুপ। মেয়েমানুষটি ঘোমটা খুলে গোবিন্দের দিকে ফিরে বলল, কিছু কি বলবে বাবা?
মুহূর্তের জন্য বিস্ময়ে আড়ষ্ট হয়ে গেল গোবিন্দ। হ্যাঁ, সেই মুখ, সেই বিশাল চোখ, তীক্ষ্ণ নাক, টকটকে রং। বয়সের ভারে সবই বিবর্ণ, ভগ্ন। রাজপুরের চক্রবর্তীদের ধর্ষিতা ভাদ্রবউ, গোবিন্দের বাবার ভৈরবী শ্মশানচারিণী। আজ হাটের ধারে মালীপাড়ায় তার বাস। কেন, সেদিনের মতো রক্তজবার অঞ্জলি কি আর তার পায়ে পড়ে না। গোবিন্দ বলল, মোর খানিক কথা ছিল তোমার সাথে।
এখানেই বলবে?
না হয় মোর ঘরে চলল।
ছি, মোরে ঘরে ডাকতে নাই।
তবে মালীপাড়ায় চলো।
সেখানে কি পারি তোমারে নিয়া যেতে? বলে এক মুহূর্ত চুপ থেকে সে বললে, না বলে যদি শাস্তি না পাও তো, চলো নয়নপুরের খালের ধারে শীতলাতলায়। সেখানে কেউ থাকবে না।
খেয়া পেরিয়ে গোবিন্দ চক্রবর্তীদের ভাদ্রবউয়ের সঙ্গে খালের ধার দিয়ে হেঁটে শীতলাতলায় চলে এল। জায়গাটা শুধু নির্জন নয়, এত নিস্তব্ধ এবং ঝোপে ঝাড়ে হওয়া যে গা ছমছম করে। একটি মস্ত হিজলগাছের তলা মাটি উঁচু করে পাথরের নুড়ি দিয়ে তাতে শীতলা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। মানুষ নেই কিন্তু দেখে মনে হয় নিয়তই কেউ শীতলাতলা লেপে পুছে পরিষ্কার করে রাখে। সেখানেই তারা উভয়ে এসে বসল।
গোবিন্দের মনে ঝড়ের এতই বেগ যে সে কোনও ভূমিকা না করেই জিজ্ঞেস করল তার বাবার সাধনার কথা, ভৈরবী জাগানোর মাহাত্ম্যের গুঢ় স্তোত্র, কারণ পান। সে শ্মশানের বীভৎস ছবি কথায় কথায় জীবন্ত হয়ে উঠল।
চক্রবর্তীদের ভাদ্ৰবউ শুনল ব কথা, শুনে জ্বলতে লাগল তার চোখ। বু সামান্য হেসে বলল, এর মধ্যে ভগবানের কী লীলা আছে আমি তো তা জানি না বাবা। সেখানে কোনওদিন ঈশ্বরও দেখি নাই, মহেশ্বরও দেখি নাই। মোর চোখে ঘোর অনাচার ছাড়া কিছুই চোখে পড়ে নাই। দেখে মনে হইত তোমার বাবার চেয়ে ঘোর ঈশ্বর অবিশ্বাসী বুঝি আর নাই। তবে, তোমার মায়ের কঠিন ব্যামো না থাকলে বাপের তোমার কি সাধ্যি ছিল আপন জীবনটারে নিয়া এমন খেলা করে? গোবিন্দর মনে হল তার হৃৎপিণ্ডটাই বুঝি গলা দিয়ে ঠেলে মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে। বলল, তবে ঠাকরুন, তুমি কী ছিলে, কেন ছিলা? তোমার পায়ে সেদিন এত ফুল চন্দনই বা কেন পড়ছিল?
ভাদ্রবউয়ের চোখে হঠাৎ আতঙ্ক দেখা দিল, আবার মিলিয়ে গেল, সে তার অতীতের দুর্ভাগ্যের কথা স্মরণ করে। তারপর বলল ফিসফিস করে কান্নাভরা গলায়, তখন মোর শেষ সব্বোনাশ হয়ে গেছে। পাছদুয়ারের পুকুরঘাটে ভর সন্ধেয় আমার গা মুখ ভরা সমস্ত রূপের গরব দলে মুচড়ে একেবারে শেষ করে দিয়ে গেল। গেছিলাম গা ধুতে, সেই সময় আচমকা ধরে আমাকে পুড়িয়ে দিয়ে গেল। কিন্তু বেঁচে রইলাম ভূত হয়ে। ঝোপে ঝাড়ে আঁধারে আঁধারে ফিরি গাঁ ঘরের বাইরে, মানুষের চোখের আড়ালে। শেষটায় স্বামীকে লুকিয়ে সব বললাম, কত অনুনয় বিনয়, কপাল কুটলাম পায়ে, পাথর গলল না। তখন তোমার বাবা একটা আচ্চয় দিল, ধম্মের আচ্চয়। ইস! কী ধম্ম! শ্মশানে মদ মাংস খেলাম, তোমার বাবার ভৈরবী হইলাম, শিবের সাথে দেবী হইলাম। কী সাংঘাতিক! গাঁয়ে ঘরের মানুষ গেছে বোগ শোক মনস্তাপ নিয়ে আশীর্বাদ ওষুধ নিতে। ফুল চন্দনের কথা বলছ? কেউ দিয়েছে বুঝে, কেউ দিয়েছে না বুঝে। বুঝে যারা দিছে তারা আজও যায় মালীপাড়ার মোর কাছে। পাপ যে এত বড় হইতে পারে তা জানতাম না।
শুনতে শুনতে হঠাৎ গোবিন্দর কাছে ভাদ্রবউয়ের দুঃখই সবচেয়ে যন্ত্রণাদায়ক ও রুদ্ধশ্বাস হয়ে উঠল। সে নির্বাক, যন্ত্রণায় বেদনায় ক্রোধে দিশেহারা।
ভাদ্রবউয়ের চোখে স্বপ্ন নেমে এল যেন, হঠাৎ পুবের গাছপালার আড়ালে চাঁদ উঠতে দেখে। ফ্যাকাসে চাঁদ সোনা হয়ে উঠছে, আগুন ধরা আকাশ। শীতলাতলার গাছ, ঝোপঝাড়ের ফাঁকে চাঁদের আলো এসে পড়েছে যেন অনেক অশরীরী আত্মার মতো। ভাদ্ৰবউ বলল, পিতি বছর এই দিনটাতে আসি রাজপুরে ঘোমটা-মোমটা টেনে। আসতে আসতে মনে হয়, পাপ তো কই করি নাই, আমি তো সোনা! হাঁ, এমন দিনেই বাপের বাড়ির গাঁয়ে সদর-পুকুরের ধারে গেছি পাথরবাটি ধুতে, কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর চিত্তির দেওয়ার পিটুলি গুলব বলে। গড়ান বেলা। ধুয়ে উঠবার মুখে দেখি এক সুন্দর পুরুষ, অ্যাই বুক, অ্যাই হাত আর কী সোন্দর চোখমুখ। কচি আম পাতার মতো নধর শ্যাম। আইবুড় মেয়ে আমি, বুক কাঁপল, পরান চমকাল। ভয়ে নয়, সে যেন আর কিছু। আর পুরুষটিরও সেই দশা। অপলক চোখে কেবল দেখল কোন্ বাড়িতে ঢুকি। তারপরেই বিয়ের সম্বন্ধ গেল রাজপুর থেকে। পুরুষ হল চক্রবর্তীদের ছোট ছেলে, আমার সোয়ামী। বাপ মোর পুজো-আচ্ছা করে খেত, তাই নিয়ে কথা উঠল। কিন্তু চক্কোত্তিদের ছোটছেলের জেদের কাছে তা হার মানল। বিয়ে হল। তারপর…
চাঁদের আলোয় চকচক করে উঠল ভাদ্রবউয়ের চোখের জল। বলল, বছরে এ দিনটাতে না এসে থাকতে পারি না। একবার তাকে দেখব বলে। সে দিনটি যে কিছুতেই ভুলতে পারি না।
হাহাকার করে উঠল গোবিন্দের বুকের মধ্যে। বলল, বলল ঠাকরুন, বলতে হইবে মোরে। কে তোমার এমন সব্বোনাশ করেছিল।
বিদ্রূপের জ্বালায় চোখ জ্বলে উঠল ভাদ্রবউয়ের। কঠিন হেসে বলল, শুনি সে নাকি এখন ব্রেহ্মজ্ঞানী হইছে, ধম্মে করছে। লোককে কালীকেষ্ট দেখায়, শিষ্যি নিয়ে মঠ-মন্দির গড়ে। দলের পাণ্ডা ছিল সেই রাজপুরের আচায্যি।
আচায্যি? আচমকা পৃথিবী ফেটে চৌচির হয়ে গেলেও বোধ করি গোবিন্দ এতখানি বিস্ময়ে চমকে উঠত না। তারপরই এক সাংঘাতিক বোবা ক্রোধে তার সমস্ত শিরা-উপশিরায় দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। আচায্যি! ধর্মগুরু আচায্যির এই সর্বনাশা কীর্তি। আর তার বাকফুরণ হল না, আর কিছু শুনতে ইচ্ছা করল না। শান্ত সাধকের হাতের পেশিগুলো ফুলে ফুলে উঠল, নিসপিস করে উঠল হাত। এখুনি কি সেই ধর্মের ষাঁড়টার মাংসল গলাটা টিপে শেষ করে দেওয়া যায় না!
ভাদ্ৰবউ শঙ্কিত হয়ে গোবিন্দর মুখ দেখে। ভাবল, না জানি কী সব্বোনাশই করেছে সে গোবিন্দকে সব কথা বলে। কিন্তু গোবিন্দ আর কোনও কথা না বলে বিদায় নিয়ে গ্রামের পথ ধরল। পেছন থেকে ভাদ্রবউয়ের গলা তার সঙ্গে এগিয়ে এল, অস্থির হয়ে কোনও সব্বোনাশ করো না বাবা। কেবল দেখো, আর কোনও আবাগীর না মোয়র মতো কপাল ভাঙে।
পুবের কোল থেকে চাঁদ খানিক উপরে এসেছে। শরৎপূর্ণিমা। বোয়া আকাশ। নীল নয়, যেন কালো কুচকুচে। গাছপালা সব চকচক করছে তবু ঝুপসি ঝাড়ে আঁধার যেন জমাট। আলোও গভীর, ছায়াও গভীর। হেমন্তের গন্ধ পাওয়া যায় সামান্য হাওয়ায়। এমনি সময় মনে হয়, এ আলো-ছায়া, শরতের ওই চাঁদ, এই বর্ণসবই যেন এক দুর্বোধ্য অজানা ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি নিয়ে চেয়ে আছে।
বাড়ির ফণীমনসার বেড়ার কাছে এসে থমকে দাঁড়াল গোবিন্দ। কে? শাড়ি পরা মেয়েমানুষ, মাথায় ঘোমটা নেই, অবিন্যস্ত বুকের আঁচল, যেন বুকের দিশা নেই। মাথা থেকে পা পর্যন্ত একটি মাত্র বঙ্কিম বিচিত্র আলোর রেখায় এক রহস্যময়ী যৌবনের ছবি আঁকা। ছায়ায় ঢাকা বাঁকা শরীরের অস্পষ্ট রেখা আরও তীব্র রহস্যঘন। গোবিন্দ দেখল বনলতা। কিন্তু একি চোখ, একী দৃষ্টি বনলতার! একী কান্না, ক্রোধ, নাকি আর কিছু? মুহূর্তে চোখ বুজল গোবিন্দ। সারা মুখে তার দরদর ধারে ঘাম বইছে, যেন জ্বরের ঘোরে কপালের শিরাগুলো স্ফীত। আহা, ভাদ্রবউয়ের সে মুখ তো ভোলা যায় না!.. আবার চোখ খুলল। ঝুঁকে পড়ল বনলতার মুখের কাছে। কই, মনে তো হয় না, এ মেয়ে ধর্মবিরুদ্ধ, অবাচীন, অসতী!
গোবিন্দর ভাব দেখে হঠাৎ শান্ত হয়ে আসে বনলতার চোখ, উৎকণ্ঠায় ভরে ওঠে বুক। দু-হাতে গোবিন্দর হাত ধরে জিজ্ঞেস করল, কী হইছে সাধু, কী হইছে তোমার?
না, আজ আর চোখ ঠারল না গোবিন্দ নিজেকে। কুণ্ঠায় ব্রাসে প্রাণ তার ধরিত্রীর অন্ধ-গর্ভ খুঁজল। নাইবা থাকল মহিম, এখুনি নাই বা পাওয়া গেল পাগলাবামুনকে। এ মেয়ের কাছেই আজ সে সব কথা বলবে। এ মেয়ে কি তার পর?
ঘরে পিসির লক্ষ্মীপুজো। লোকজনের সাড়া পাওয়া যায় বাড়ির ভিতরে। বৃদ্ধ নসীরামও আজ মেতেছে। সেবাদাসী সরযুর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে সে গান ধরেছে।
বনলতার সঙ্গে গোবিন্দ এল আখড়ার পিছনে ডাহুকের আস্তানায় ডোবার ধারে। সেখানে বসে উত্তেজনায় আবেগে সব কথা সে বলে গেল বনলতার কাছে। বলতে বলতে আবার বোবা ক্রোধে থমথমিয়ে উঠল গোবিন্দ। বলল, আচায্যিরে খুন করব মুই।
আশ্চর্য শান্ত আর মমতাময়ী হয়ে উঠেছে বনলতা। শঙ্কিত গলায় বলল, ছি খুনের কথা বলে। আচায্যিরে ত্যাগ দেও তুমি। ওর ধম্মের ভোল ভেঙে দেও।
কিন্তু আবার কান্নায় ভরে উঠল গোবিন্দর গলা। বলল, মায়ের কথা মোর মনে হইলে বুকটা ফেটে যায়রে লতা। সে পাপের বুঝি চিত্তির নাই।
এর বাড়া প্রাচিত্তি আর কী হবে সাধু? বলে বনলতা হাত রাখল গোবিন্দর উষ্ণ কপালে।
সাধু নয়, মোরে গোবিন্দ বলে ডাক লতা।
ও নাম মোরে নিতে নাই।
সহসা যেন নতুন গলার স্বরে চমকাল গোবিন্দ। নিঃসীম আকাশে শরতের চাঁদ যেন কুহেলিকা। তার আলোয় বনলতার মুখও কুহেলিকাপূর্ণ। ঠোঁটে হাসি ফুটল বিচিত্র, চোখে মোহিনীলীলা। তার উষ্ণ নিশ্বাস লাগল গোবিন্দর গলায় গালে। তার সারা শরীর কাঁপল। বুঝি চকিতে সেই কুণ্ঠাও এল। কেবলি মনে হল, এ মেয়ে কি তার পর? বলল, ছোটকালে তুই তো মোরে নাম ধরে ডাকতিস?
ছোটকাল যে আর নাই। বলতে বলতে সেই দুরন্ত মেয়ে বনলতাও আজ গোবিন্দর চোখের উপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিল।
গোবিন্দ বলল, তবে কী আছে?
মোরা আছি।
সেই তেমনি?
না। নতুন ধারা।
বনলতার পাতা হাঁটুর উপর দু’হাত রেখে খানিকক্ষণ স্তব্ধ থেকে যেন বহুদুর থেকে বলল গোবিন্দ, জগতের তালটা ধরতে পারি না, মোরে খানিক তুলে ধর তো বনলতা।
বনলতা তার প্রজাপতির ঝাপটা খাওয়া খালি বুকটায় গোবিন্দর মাথাটা চেপে ধরল। গোবিন্দর এ আত্মসমর্পণে কান্নায় বুকটা ভরে উঠল তার। জড়ানো দুহাতে তার সতেজ বনলতার মহীরুহ বেষ্টনীর উল্লাস।
এমনিভাবে বুঝি ধরিত্রীর গর্ভে নতুন ভ্রূণ সঞ্চারিত হয়।
ঝোপের ছায়ায় আখড়ার বেড়ায় হেলান দিয়ে বনলতার অন্তর্যামী নরহরি সে দৃশ্য দেখল। অন্তর্যামী বলেই বোধ হয় তারও মুখ হাসিজলে মাখামাখি। গলায় সুর কেঁপে উঠল তার। কিন্তু না, সখী বাধা পাবে গলার স্বরে। আখড়ায় ঢুকে সকলের আড়ালে একতারাটি নিয়ে সে তেপান্তরের পথ ধরে খালের মোহনার দিকে এগুল। বিরহ নয়, বুক উজাড় করে মিলনগাথাই গাইবে সে আজ।
কিন্তু ভাদ্রবউয়ের অনুরাগে ভরা এ রাত্রি যেন কী খেলা শুরু করেছে।
এমনি সময়ে মহিম উমার ঘরে, উমার পাশে অর্ধচেতন বিহ্বল মূক হয়ে বসে উমার উদ্বেলিত আবেগ উত্তেজনার কাকুতি শুনেছে।
তেপান্তরের ধারের সেই জানালা দিয়ে ঝাঁপ দিয়েছে চাঁদের আলো ঘরের মধ্যে। রাজপুরের ধূসর রেখা, দূর আকাশে হেমন্ত কুয়াশার পাতলা আভাস। প্রাণবন্ত শারদরাত্রি, শরতের শ্রেষ্ঠ দিনটি। শিউলিফুলের মোহিনীগন্ধ যেন লেপটে রয়েছে সর্বত্র। দিন ভেবে পাখি ডাকে আলো ভরা বাসা থেকে। ভেসে আসে লক্ষ্মীপুজোর কাঁসর ঘন্টার শব্দ। এ বাড়িতেও আজ পুজো। নীচে চলেছে সে উৎসব, ঝি চাকরের হাতে সব ভার। খাটছে আমলা কামলারা। গৃহিণী লক্ষ্মী অভিসারে মত্ত।
উমা আজ সশস্ত্র। মারণাস্ত্র তার সর্বাঙ্গে, চোখে মুখে বেশে। সে অস্ত্র অদৃশ্যে অন্তর ঘায়েল করে। অজ পাড়াগাঁ নয়নপুরের শিল্পীকে ঘায়েল করার জন্য এই আয়োজন। কিন্তু কেন? শিল্পীর জীবনকে উন্নত মর্যাদাময় আসনে প্রতিষ্ঠা করার জন্য? দেবতার জন্য ভক্তিমতীর একী আয়োজন! হ্যাঁ, বর প্রার্থনার কৌশলই বুঝি এই যে, দেবতার সমস্ত চেতনাকে গ্রাস করতে হরে।
ঘরের এক কোণে নিষ্কম্প স্তিমিত আলো। দরজা বন্ধ। সমস্ত মহল নিস্তব্ধ, কেবল যেন অনেক অদৃশ্য মানুষের পদশব্দের ধুপধাপ শব্দ শোনা যায়।
উমার সর্বাঙ্গে একটিও গহনা নেই, বাঁধা নেই চুল। সবই যেন অগোছাল। চোখে বহি, প্রাণে বহি, বহ্নিময়ী উমা। সেই বহ্নি ডাক দিয়েছে মহিমকে। উমা বলে চলেছে শিল্পীর জীবনের ভবিষ্যৎ, দুনিয়া-জোড়া যার নাম, পথে পথে যার পরিচয়, ঐশ্বর্য, সুখ একটানা সুখের জীবন। গ্রাম নয়, শহর। নয়নপুর নয়, কলকাতা। বোধ করি এ মন্ত্রেরই পাশে পাশে যে কথাটি চাপা আছে তা মণ্ডলবউ অহল্যা নয়, শহরের ধনী বিদুষী উমা।
কিন্তু মহিমের অসহায় বুকে ত্রাস, অবিশ্বাস। বিদ্যুতের মতো চমকে চমকে উঠছে অহল্যার চোখ, নিষ্ঠুর বঙ্কিম ঠোঁট অথচ কান্নাভরা। কলকাতা, পাগলা গৌরাঙ্গের কাছ থেকে চলে আসার দিন সেই চোখের জল, আলিঙ্গন। শৈশব থেকে যৌবন, এক বিচিত্র বন্ধন গড়ে উঠেছে। কী জানি, কী সে বন্ধন। তবু নাড়ির টান যেন! দুর্বোধ্য মন শুধু বলে, অহল্যা বউ যে। আর এই নয়নপুর, রাজপুর, খাল, মাঠ, সবার বড় তার মানুষ, হরেরামদা, অখিল, পীতাম্বর, ভজন, কুঁজো কানাই, অর্জুন পাল, গোবিন্দ, বনলতা, আখড়া—এমন কী তার দাদা ভরত, তার প্রাণকেন্দ্রের বেড়া। যেখান থেকে হাত বাড়ালে মাটি পাওয়া যায়।
সে বলল মাথা নিচু করে, না, নয়নপুর ত্যাগ দেওয়া মোর হইবে না।
সে কথায় বহ্নিশিখা আরও লেলিহান হয়ে উঠল। সমস্ত শরীরে চাঁদের আলো নিয়ে দাঁড়াল উমা। বঙ্কিম ঠোঁটে মর্মঘাতী হাসি, বিলোল কটাক্ষ করে এক হাতে মহিমের চিবুক তুলে ধরে বলল, ভয় পেয়েছ? কেন? তোমার জীবনটা বড় হোক, আমার এ চাওয়া কি ভুল?
না।
তবে?
মহিম তাকাল চোখ তুলে। বুকের মধ্যে ককিয়ে উঠল তার। সামনে যেন তার আগুনের শিখা দুলছে। আবছায়াতে আধো-আড়াল করা উমার সুগঠিত বুকের অতল রহস্যের ঢেউ উকি। হাত দিয়ে মহিমকে টেনে ধরে উমা বলল, আমি তোমার শিল্পের ভক্ত, নয় কি?
হ্যাঁ।
তুমি প্রতিষ্ঠা চাও না?
চাই।
আমাকে চাও না?
মহিম নীরব।
উমা বলল, আমার ভক্তি তুমি চাও না?
চাই।
তবে তোমার প্রতিষ্ঠার জন্য আমাকে কিছু করতে দেবে না?
দেব।
তবে চলো কলকাতা।
মহিম নির্বাক। কিন্তু উমা শিল্পীর গুণটুকু ছেড়ে শিল্পীকেই গ্রাস করতে চায় যেন। একী প্রাণের লীলা যে, শিল্পীকেই টেনে নিতে চায় সে। বিদুষী, ধনী, জমিদারের পুত্রবধু উমা, নিজেকে চেনে না। কিন্তু অজপাড়াগাঁয়ের এ চাষী ছেলেকেই কি চেনে?
উমা বলল, জমিদারের মাইনে নিয়ে থাকতে চাও তুমি?
না।
তবে কীসের প্রত্যাশা তোমার এখানে? কী সুখের আশায়?
মহিম অসহায় নিরুত্তর। কোনও সুখের প্রত্যাশাই তো তার নেই।
হঠাৎ উমা তীক্ষ্ণ গলায় ঢেউ দিয়ে বলল, তোমার বউদি দুঃখ পাবে, তাই?
মহিম বলল, নয়নপুর মুই পারি না ছাড়তে।
উমার ধৈর্যের বাঁধ ভাঙল। বলে উঠল, নাঃ, ঘোটলোক কখনও মানুষ হয় না। নিজেদের ভাল-মন্দও কি তোমরা বুঝতে পারো না?
শুধু চমকাল না মহিম। বিস্মিত বেদনায় স্তব্ধ হয়ে গেল। বুকের মধ্যে জ্বলে গেল অপমানে, সিঁটিয়ে গেল ঘৃণায়। একটু চুপ থেকে বলল, আমি যাই তা হইলে?
আবার উমা পেখম খোলে। বলল, আমি তোমার বন্ধু, বোঝো না?
বুঝি।
তোমাকে ডেকে আনি জানলে আমার শ্বশুর রুষ্ট হবে, তবু ডাকি, জানো তুমি?
জানি।
তবে আমাকে কি খারাপ মানুষ ভাবো?
মহিম তাড়াতাড়ি বলে উঠল, তা কী করে হয়?
তবে?
মোরে মাপ করেন।
না, সুন্দরের ভক্ত মহিম, উমার কাছে সে রুষ্ট হতে জানে না।
উমা বলল, বাইরে পরান আছে, দরজা খুলে যাও। তারপর আপনমনেই বলে উঠল, চাষার গোঁ, মাটি কাটা ছাড়া আর কিছু হবে না। শুনল সে কথা মহিম।
উমা তাকিয়ে রইল মহিমের চলমান শরীরটার দিকে। নরম শ্যামল মিষ্টি শিল্পী। কিন্তু দেহের কোথায় যেন একটা কঠিন ভঙ্গি ফুটে রয়েছে। দরজা খুলে বেরিয়ে যাওয়ার মুখে আচমকা ছুটে গিয়ে দুহাতে সাপটে ধরল উমা মহিমকে। বলল, প্রণাম করলে না আজ?
মহিম রুদ্ধশ্বাস, অগ্নিদগ্ধের মতো ফ্যাকাসে হয়ে গেল সেই বাহুবেষ্টনীর মধ্যে। তাকাল। চোখে যেন দেখল, তাকে নিয়ত আড়াল করা অহল্যা বউয়ের মুখ। ঝুঁকে পড়ল সে পায়ে হাত দেওয়ার জন্য! বাধা দিয়ে উমাই দুহাত আটকে রাখল তার বুকে। বলল, ডাকলে আসবে তো?
আসব।
হাত ছেড়ে দিয়ে উমা ভাবল, এটা তার নিয়তি!
বিস্ময় আর অপমান শুধু নয়, এক দুর্বোধ্য বোবা জ্বালায় প্রাণটা পুড়তে লাগল মহিমের। কান দুটো এখনও জ্বলতে লাগল উমার কথাগুলো মনে করে। একবার মনে হল, সবটাই প্রলাপ। উমার আবেগ, রাগ সবই। আবার মনে হল, না, তাকে অপমান অপদস্থ করাই জমিদারের ছেলের বউয়ের একমাত্র উদ্দেশ্য। কিন্তু তার সমস্ত বুক, হাত যেন জ্বলে যাচ্ছে। আগুনের আলিঙ্গন ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে সে। কী যেন ঠেলে আসছে গলার কাছে, বুঝি কান্না পাচ্ছে। একী অভাবনীয় ব্যাপার। এমন অবাস্তব, এমন অসম্ভব সম্ভব হল কী করে যে উমার মতো মেয়ে তাকে আলিঙ্গন করতে চায়?
না, সে কথা বুঝবে না মহিম। যে উমা তাকে অমন করে চেয়েছে সে বিদুষী নয়, অভিজাত নয়, বুঝি জমিদারের পুত্রবধূও নয়। সে এক প্রেমকাঙালি মেয়ে। কিন্তু তার ভয় বেশি, ক্ষুধা তার সর্বগ্রাসী, সংসারের প্রতি তার অবিশ্বাসই শিল্পীকে মূল থেকে উপড়ে টেনে তোলার উত্তেজনা জুগিয়েছে।
পরান গেট অবধি পৌঁছে দিয়ে গেল তাকে। মহিম টলতে টলতে ঘুরপথে বাড়ি ফিরে চলল।
কী রাত! উমার ঘর থেকে দেখা রাত্রির কোনও পরিবর্তনই চোখে পড়ল না মহিমের।
কিন্তু এ রাত যেন ভাদ্রবউয়ের প্রাণের হাহাকার ভরা রাত্রি।
মহিম দেখল, একটা ঝোপঝাড়ের অন্ধকার ছায়ায় কী যেন নড়ছে। দেখল, হাত দুলিয়ে মাথা নাড়ছে কুঁজো কানাই। অদূরে কালুমালার মেয়ে উঠোনের নিকনো কুরচিতলায় বসে কাঁদছে এই লক্ষ্মীপূর্ণিমার ভর রাত্রে। লুকিয়ে তাই দেখছে কুঁজো কানাই।
মহিম কোনও কথা বলল না, ডাকল না কানাইকে। কেবল তার বুকের যেটুকু বাকি ছিল, সেটুকুও ভরে উঠল উঠল জ্বালায়। আরও দ্রুত মহিম পা চালাল ঘরের দিকে।
উঠোনে এসেই দেখল অহল্যা তার ঘরের দাওয়ায় এদিকে তাকিয়েই বসে আছে! মুহূর্ত স্তব্ধতা। যেমন করে কলকাতায় পাগলা গৌরাঙ্গের ঘরে ছুটে গিয়েছিল মহিম অহল্যাকে দেখে, আজও তেমনি শিশুর মতো ছুটে গিয়ে অহল্যার কোলের উপর দু-হাতে মুখ ঢেকে নীরব দুরন্ত কান্নায় ভেঙে পড়ল সে।
আশ্চর্য! অহল্যা চমকাল না, বিস্মিত হল না। যেন সবটাই তার জানা ছিল। দু-হাতে মহিমের পিঠে মাথায় গভীর স্নেহে বোলাতে লাগল সে, আর ঠোঁটে ঠোঁটে টিপে শক্ত করে রাখল নিজেকে। কেবল চোখ দুটোকে কিছুতেই স্বচ্ছ রাখতে পারল না।
এমনি কাটল কিছুক্ষণ। .মহিম রক্তিম ভেজা চোখ তুলল, অহল্যার দিকে। মাথায় কাপড় নেই অহল্যার, কাঁধ খোলা। বিশাল বুক ঢাকা কাপড় বগলের পাশ দিয়ে অন্তর্ধান হয়েছে। কপালে জ্বজ্জ্বল করছে সিঁদুরের টিপ। নির্নিমেষ চোখে জল। মহিমের গালে হাত বুলিয়ে বলল, মোরে কিছু বলতে হইবে না।
হ্যাঁ, বলতে হইবে।
মহিমের গলার স্বর শুনে চমকে তাকাল অহল্যা। বলল, কী বলবে?
মহিম বলল, শরীলটা জ্বলে যাচ্ছে।
অহল্যা একেবারে আড়ষ্ট হয়ে গেল। হায়, এ কী সর্বনাশা চোখ হয়েছে মহিমের। শিশু নয়, কিশোর নয়, দুর্দম যুবক। চোখে তার আগুন। দুরদুর করে উঠল অহল্যার বুক, মুখটা পুড়ে যেন ছাই হয়ে গেল। সে ডাকল তীব্র চাপা গলায়, ঠাকুরপো!
মহিম নির্বাক, আতুর।
অহল্যা ডাকল, মহী!
যেন ন’বছরের বউ পাঁচ বছরের দেবরকে শাসনের ডাক দিল।
মহিম বলল, কী?
অহল্যা দু-হাতে মুখ ঢেকে বলল, মোরে কি গলায় দড়ি দিতে হইবে?
চকে পেছিয়ে এল মহিম। কেন?
নয় তো কী?
কী যেন হৃদয়ঙ্গম করে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো ফিরে মহিম তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।
অহল্যা ভেঙে পড়ল কান্নায়। বাঁধভাঙা পূর্ণিমার আলোর মতো কামায় ড়ুবে গেল সে।
তারপর অনেকক্ষণ বাদে উঠে সে ডাক দিল, ঠাকুরপো, খাবে না?
ভেতর থেকে জবাব এল না। কান পেতে শুনল অহল্যা মহিমের ঘুমন্ত নিঃশ্বাস।
অহল্যা এল নিজের ঘরে। ভরত ঘুমোচ্ছে। কিন্তু অহল্যার চোখ যেন শাপদের মতো জ্বলছে অন্ধকার ঘরে। একটু দাঁড়িয়ে থেকে ধীরে ধীরে বিছানার কাছে এসে হঠাৎ ভরতের বুকের উপর মাথা রেখে শুয়ে পড়ল সে।
ভরতের ঘুম ভেঙে গেল। বলল, কী রে বউ?
অহল্যা নীরব।
ভরত বলল, মহী আসে নাই জমিদার বাড়ি থে?
আসছে।
তবে কি মানিক ছোঁড়া ভাত খেতে আসে নাই?
আসছিল। খানিকক্ষণ চুপ থেকে ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেলে ভরত বলল, কাল আদালত থে আসবার সময় লবপুরের ধনাই ফকিরের মাদুলি একটা নিয়া আসব, সেধে তোর ছাওয়াল আসবে।
এবার অহল্যার অবুঝ কান্নায় বুক ভাসল ভরতের।
আহা, বাঁধা বীণার তারে বেসুর কী গভীর!