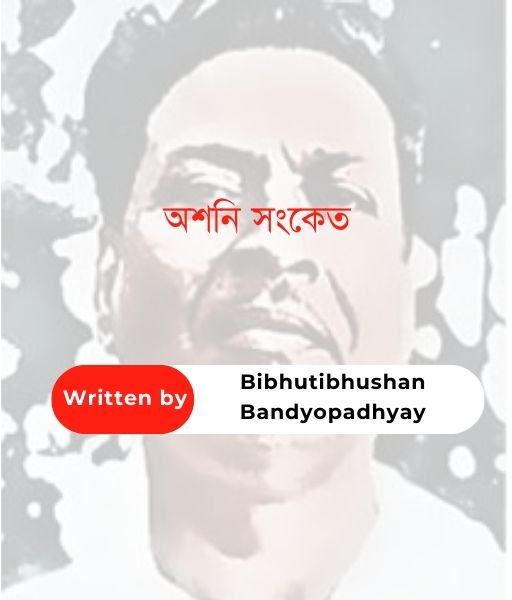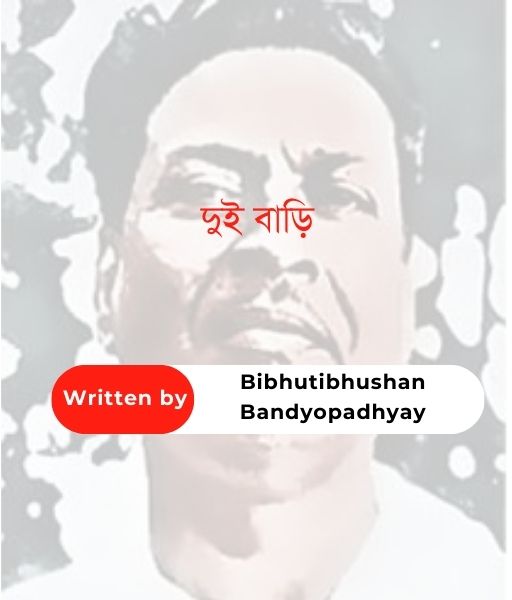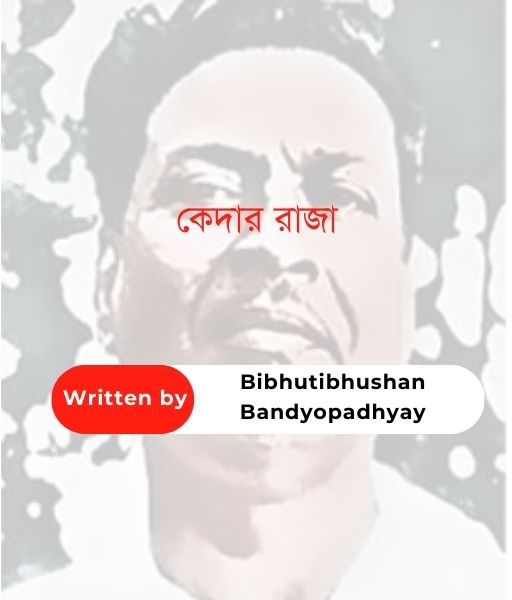পৌষ মাসের শেষে
০৫.
পৌষ মাসের শেষে আমাদের বাড়ি সরগরম হয়ে উঠল–শুনলাম ওঁদের গুরুদেব আসবেন বলে চিঠি লিখেছেন।
এই গুরুদেবের কথা আমি এঁদের বাড়িতে এর আগে অনেক শুনেচি–জ্যাঠামশায়ের ঘরে তাঁর একটা বড় বাঁধানো ফটোগ্রাফ দেখেছিলাম–গুরুদেব চেয়ারে বসে আছেন, জ্যাঠামশায় ও জ্যাঠাইমা দুজন দু-দিকে মাটিতে বসে তাঁর পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিচ্ছেন। অনেক দিন থেকে ছবিখানা দেখে গুরুদেব সম্বন্ধে আমার মনে একটা কৌতূহল হয়েছিল–কিরকম লোক একবার দেখবার বড় ইচ্ছে হত।
স্টেশনে তাঁকে আনতে লোক গিয়েছিল–একটু বেলা হ’লে দেখি দাদা এক ভারী মোট বয়ে আগে আগে আসচে-পেছনে ব্যাগ-হাতে জ্যাঠামশায়দের কৃষাণ নিমু গোয়ালা। গুরুদেব হেঁটে আসচেন, রং কালো, মাথার সামনের দিকে টাক–-গায়ে চাদর, পায়ে চটি। আমার জাঠতুতো, খুড়তুতো ভাইবোনেরা দরজার কাছে ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল–পায়ের ধুলো নেওয়ার জন্যে তাদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। আমি এগিয়েও গেলাম না, পায়ের ধুলোও নিলাম না। জ্যাঠাইমা গুরুদেবের পা নিজের হাতে ধুইয়ে আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিলেন, খুড়ীমারা বাতাস করতে লাগলেন–ছেলে-মেয়েরা তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রইল, তিনি সেজ-খুড়ীমাকে জিজ্ঞেস করলেন–বৌমা, ছেলের তোতলামিটা সেরেচে? মেজখুড়ীমাকে বললেন–গোষ্ঠ মেজকাকার নাম আজকাল কি বাদার কাছারী থেকে গরমের সময় একদম আসে না?..কতদিন আগে এসেছিল বললে?
বাড়ির ছেলেমেয়েদের একে ওকে ডেকে মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করলেন, দু-একটা কথা জিজ্ঞেস করলেন–কিন্তু দাদা যে অত বড় ভারী মোট বয়ে আনলে স্টেশন থেকে, সে-ও সেইখানে দাঁড়িয়ে–তাকে একটা মিষ্টি কথাও বললেন না। আমার রাগ হ’ল, তিনি কি ভেবেচেন দাদা বাড়ির চাকর? তাও ভাবা অসম্ভব এইজন্যে যে, ওখানে যতগুলো ছেলেমেয়ে দাঁড়িয়ে ভিড় করে আছে, তাদের মধ্যে দাদার রূপ সকলের আগে চোখকে আকৃষ্ট করে-এ গায়ে দাদার মত রূপবান বালক নেই, শুধু এ বাড়ি তো দূরের কথা। আশা করে দাঁড়িয়ে আছে, একটা ভাল কথাও তো বলতে হয় তার সঙ্গে?
গুরুদেবের জন্যে বিকেলে বাড়িতে কত কি খাবার তৈরি হ’ল–মেজখুড়ীমা, সদুর-মা, জ্যাঠাইমা–সবাই মিলে ক্ষীরের, নারিকেলের, ছানার কি সব গড়লেন। মাকে এ-সব কাজে ডাক পড়ে না, কিন্তু দেখে একটু অবাক হলাম সদুর মাকে ওঁরা এতে ডেকেচেন। মা আর সদুর মা’র ওপর যত উঞ্ছ কাজের ভার এ বাড়ির। সদুর মা’র অদৃষ্ট ভাল হয়েচে দেখচি।
গুরুদেব সন্ধ্যা-আহ্নিক সেরে বাইরে এলে তাঁকে যখন খাবার দেওয়া হ’ল, তখন সেখানে বাড়ির ছেলেমেয়ে সবাই ছিল–আমরাও ছিলাম। কিন্তু হিরণদিদি ও সেজকাকীমা সকলকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দিলেন। গুরুদেব বললেন–কেন ওদের যেতে বলচ বৌমা, থাক না, ছেলেপিলেরা গোলমাল করেই থাকে–
গুরুদেব তিন-চারদিন রইলেন। তাঁর জন্যে সকালে বিকালে নিত্যনূতন কি খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থাই যে হ’ল! পিঠে, পায়েস, সন্দেশ, ছানার পায়েস, ক্ষীরের ছাঁচ, চন্দ্রপুলি, লুচি–তিনি তো খেতে পারতেন না–আমরা বাদে বাড়ির অন্য ছেলেমেয়েরা তাঁর পাতের প্রসাদ পেত। তিনি জলখাবার খেয়ে উঠলে তাঁর রেকাবিতে বা থালায় যা পড়ে থাকত, কাকীমারা ডেকে ছেলেমেয়েদের দিতেন–আমরা সেখানে থাকতাম না–কারণ প্রথম দিকে ছেলেমেয়েরা সেখানে থাকলে কাকীমা বকতেন–তার পর গুরুদেবের খাওয়া হয়ে গেলে যখন তাদের ডাক পড়ত, তখন বাড়ির ছেলেরা কাছেকাছেই থাকতো ব’লে তারাই যেত–আমি কারুর পাতের জিনিস খেতে পারিনে, এই জন্যে আমি যেতাম না। ওঁরা ডেকেও কোনো খাবার জিনিস আমাদের কোনো দিন দিলেন না–কিন্তু মনে মনে আমি হতাশ হলাম–আমি একেবারে যে আশা করিনি তা নয়, ভেবেছিলাম গুরুদেব এলে আমরা সবাই ভাল খাওয়ার ভাগ পাব কিছু কিছু।
সন্ধ্যাবেলা। বেশ শীত পড়েছে। গুরুদেব আমলকীতলায় কাঠের জলচৌকিতে কম্বল পেতে বসে আছেন। গায়ে সবুজ পাড়-বসানো বালাপোশ-ছেলেমেয়েরা সব ঘিরে আছে, যেমন সর্বদাই থাকে একটু পরে জ্যাঠাইমা, মেজকাকীমা, সদুর মা, হিরণদিদি এলেন।
গুরুদেবের খুব কাছে আমি কোনো দিন যাইনি–আমি গোয়ালঘরের কাছে দাঁড়িয়ে আছি, ছেলেমেয়েরা গল্প শুনচে গুরুদেবের কাছে, আমার কিন্তু গল্পের দিকে মন নেই, আমার জানবার জন্যে ভয়ানক কৌতূহল যে গুরুদেব কি ধরনের লোক, তাঁর অত খাতির, যত্ন, আদর এরা কেন করে, তাঁর পায়ে জ্যাঠাইমা ও জ্যাঠামশায় পুস্পাঞ্জলি দেনই বা কেন, তাঁর ফটো বাঁধিয়েই বা ঘরে রাখা আছে কেন? এসবের দরুন গুরুদেব সম্বন্ধে আমার মনে এমন একটা অদ্ভুত আগ্রহ ও কৌতূহল জন্মে গিয়েছে যে, তিনি যেখানেই থাকুন, আমি কাছে কাছে আছি সর্বদাই–অথচ খুব নিকটে যাইনে!
গুরুদেব মুখে মুখে ধর্মের কথা বলতে লাগলেন। আমি আর একটু এগিয়ে গেলাম ভাল করে শোনবার জন্য। এ-সব কথা শুনতে আমার বড় ভাল লাগে।
একবার কি একটা যোগ উপস্থিত–গঙ্গাস্নানে মহাপুণ্য, সকল পাপ ক্ষয় হয়ে যাবে, স্নান করলেই মুক্তি। পার্বতী শিবকে বললেন–আচ্ছা প্রভু, আজ এই যে লক্ষ লক্ষ লোক কাশীতে স্নান করবে, সকলেই মুক্তি পাবে? শিব বললেন, তা নয় পার্বতী। চলো তোমায় দেখাব।
দুজনে কাশীতে এলেন মণিকর্ণিকার ঘাটে। শিব বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের শব সেজে ঘাটের ধারে পড়ে রইলেন। পার্বতী তাঁর স্ত্রী সেজে পাশে বসে কাঁদতে লাগলেন। যারা এল, তাদের বললেন আমার বৃদ্ধ স্বামী মারা গিয়েছেন, এর সৎকার করার ব্যবস্থা আপনারা করুন। কিন্তু একটা মুশকিল আছে, শব যিনি স্পর্শ করবেন, তাঁর সম্পূর্ণ নিষ্পাপ হওয়া চাই, নইলে শব-স্পর্শেই মৃত্যু ঘটবে।
এ-কথা শুনে সাহস করে কেউ এগোয় না। সবাই ভাবে পাপ তো কতই করেচি। প্রাণ দিতে যাবে কে? সারাদিন কাটলো। সন্ধ্যা নামে-নামে। একজন চণ্ডাল ঘাটের ধারে অশ্রুমুখী ব্রাহ্মণপত্নীকে দেখে কি হয়েছে জিজ্ঞাসা করলে। পার্বতী সকলকে যা বলে এসেছেন তাকেও তাই বললেন। চণ্ডাল শুনে ভেবে বললে–তার জন্য ভাবনা কি মা? আজ গঙ্গাস্নান করলে তো নিষ্পাপ হবোই, এত বড় যোগ যখন, এ জন্ম তো দূরের কথা শত জন্মের পাপ ক্ষয় হয়ে যাবে পাঁজিতে লিখেচে। তা দাঁড়ান, আমি ডুবটা দিয়ে আসি এবং একটু পরেই ডুব দিয়ে উঠে এসে বললে–মা ধরুন ওদিক, আমি পায়ের দিকটা ধরচি–চলুন নিয়ে যাই।
শিব নিজমূর্তি ধারণ করে চণ্ডালকে বর দিলেন। পার্বতীকে বললেন–পার্বতী দেখলে? এই লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে এই লোকটি মাত্র আজকের যোগের ফল লাভ করবে। মুক্তি যদি কেউ পায় এই চণ্ডালই পাবে।
গল্পটা আমার ভারি ভাল লাগল। সে-দিনকার চৈতন্যচরিতামৃতে পড়া সেই কথাটা মনে পড়ল–জ্যাঠাইমাকে বলেছিলাম, জ্যাঠাইমা বিশ্বাস করেন নি। ওঁদের শাস্ত্রের কথাতেই ওঁর বিশ্বাস নেই। অথচ মুখে হিন্দুয়ানি তো খুব দেখান! আর আমাকে, মাকে, সীতাকে, দাদাকে বলেন খিরিস্টান।
আজযের গুরুদেবের এই গল্পটা কি জ্যাঠাইমা কাকীমারা বুঝতে পারলেন? চণ্ডালের ওপর আমার ভক্তি হ’ল। আমি যেন মনে মনে কাশী চলে গিয়েচি, আমি যেন মণিকর্ণিকার ঘাটে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবেশী শিব ও ক্রন্দনরতা পার্বতীকে প্রত্যক্ষ করেছি।
ও-বছর বড়দিনের সময় মিশনারী মেয়েরা আমাদের রঙীন কার্ড দিয়েছিল, ছোট একখানা ছবিওয়ালা বই দিয়েছিল। তাতে একটি কথা সোনার জলে বড় বড় করে লেখা আছে মনে পড়ল–তাহারা ধন্য যাহারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। কারণ তাহারা জীবনমুকুট প্রাপ্ত হইবে।
তার পরদিন সন্ধ্যাবেলাতেও গুরুদেব আমলকীতলায় আসন পেতে বসে গল্প বলছিলেন ছেলেমেয়েদের। একবার উঠে আহ্নিক করতে গেলেন, আবার এসে বসলেন। মেয়েরাও এলেন।
কথা বলতে বলতে হঠাৎ আমার দিকে আঙুল দিয়ে বললেন–ও ছেলেটি কে? রোজ দেখি দাঁড়িয়ে থাকে। এস এস বাবা, এদিকে এস।
প্রথমটা আমার বড় লজ্জা হ’ল কিন্তু কেমন একটা আনন্দও হ’ল। একটু এগিয়ে গেলাম। জ্যাঠাইমা বললে–ও আমার এক খুড়তুতো দেওরের ছেলে। ওরা এখানে থাকতো না, চা-বাগানে ওর বাবা কাজ করতো। এখানে এসে অসুখ হয়ে মারা গেল আর তো কেউ নেই, ওরা এ বাড়িতে থাকে।
গুরুদেব বললেন–এস দেখি বাবা, হাতটা দেখি, সরে এস। তারপর জ্যাঠাইমাদের দিকে চেয়ে বললেন–খুব লক্ষণযুক্ত ছেলে। এর বয়স কত?
আমায় লক্ষণযুক্ত বলাতে–বিশেষত অত ছেলের মাঝ থেকে-জ্যাঠাইমা কাকীমারা নিশ্চয়ই খুব খুশি হননি। জ্যাঠাইমা প্রমাণ করবার চেষ্টা করলেন আমার বয়স নাকি পনেরো বছর–আমি ওঁর ছেলে হাবুর চেয়েও দেড় বছরের বড়। আসলে আমার বয়স তেরো–জ্যাঠাইমার বড় ছেলে হাবুকে আমরা হাবুদা বলে ডাকি, সে আমাদের সবার চেয়ে দু-বছরের বড়। স্কুলে তার যা বয়েস লেখানো আছে, তাই ধরে বলচি।
তারপর গুরুদেব আমায় জিজ্ঞেস করলেন–কি পড় বাবা?
আমি কোন ক্লাসে পড়ি বললাম।
ধাতুরূপ কতদূর পড়েচ? লুঙ লিট বোঝ? এই শোনো একটি শ্লোক-
সোধ্যৈষ্ট বেদাংস্ত্রিদশানষ্ট
পিতৃতার্প্সীৎ সমমংস্তে বন্ধুন
ব্যজৈষ্ঠ ষড়বর্গমরংস্ত নীতৌ
সমূলঘাতংন্যবধীদরীংশ্চ।
হেসে বললেন—কত রকম ধাতুর ব্যবহার দেখেছ? এ হ’ল ভট্টিকাব্যের শ্লোক।
আমার বেশ ভালো লাগলো, গুরুদেবকেও এবং তাঁর শ্লোককেও। আমি এর আগে সংস্কৃত শ্লোক বেশি শুনিনি। চা-বাগানে কেউ বলতো না। শ্লোকটা আমি মুখস্থ করে নিলাম।
একদিন তিনি বাড়ির পাশের মাঠে শুকনো পাতা দিয়ে আগুন জ্বেলেচেন। আমায় দেখে বললেন–এসো জিতু–
আমি বললাম–কি করবেন আগুন জ্বেলে?…
—তামাক পোড়াবো!
— আমি বললাম, আমি পুড়িয়ে দিচ্চি।
গুরুদেব অনেক সংস্কৃত শ্লোক আমাকে শোনালেন। কুবেরের শাপে এক যক্ষ গৃহ থেকে বহুদূরে কোন পর্বতে নির্বাসিত হয়েছিল, বাড়ির জন্যে ভেবে ভেবে তার হাতের সোনার বালা ঢল হয়ে গিয়েছিল, তারপর আষাঢ় মাসের প্রথম দিনে সেই পাহাড়ের মাথায় বর্ষার নতুন কালো মেঘ নামল–এই রকম একটা, শ্লোকের মানে। আমি তো সংস্কৃত পড়ি মোটে ঋজুপাঠ, কিন্তু আমাকেই তিনি আগ্রহের সঙ্গে এমনি ভাল ভাল অনেক শ্লোক শোনাতে লাগলেন–যেন আমি কত বুঝি!
এবার মনে হল আমার নিজের কথা যা কাউকে কখনও বলিনি এ পর্যন্ত–তাঁর কাছে খুলে বলি, আমার মনের সন্দেহ, আমার ঐসব অদ্ভুত জিনিস দেখার ব্যাপার, জ্যাঠাইমাদের সঙ্গে আচার-ব্যবহার নিয়ে আমার মত না মেলা,–সকলের ওপর ঠাকুরদেবতা সম্বন্ধে আমার অবিশ্বাস–এসব খুলে বলে তিনি কি বলেন শুনি। তাঁর ওপর এমন একটা শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস হয়ে গেল আমার! যেন মনে হ’ল এঁর কাছে বললে ইনি সব বুঝিয়ে দিতে পারবেন আমাকে। এত বড় লোক ইনি, এত পণ্ডিত, কত কথা জানেন!
কিন্তু সুবিধে হ’ল না। বলি-বলি করেও বলতে আমার কেমন লজ্জা হ’ল। তিন দিন এমনি কেটে গেল, তারপর তিনি চলে গেলেন।
আমার কিন্তু বলতে পারলেই ভাল হত। একজন ভাল লোককে আমার সব কথা বলা দরকার। অথচ এখানে তেমন কোন লোককে আমি বিশ্বাস করিনে–কারুর ওপর আমার ভক্তি হয় না।
আমি আজকাল নির্জনে বসলেই অদ্ভুত জিনিস সব দেখি। যখন তখন, তার সময় নেই অসময় নেই, রাত নেই দিন নেই। এই তো সেদিন বসে আছি জ্যাঠাইমাদের পুকুরধারের বাগানে একলাটি–হঠাৎ দেখি পুকুরপাড়ের আমগাছগুলোর ওপরকার নীল আকাশে একটা মন্দিরের চুড়ো–প্রকাণ্ড মন্দির, রোদ লেগে ঝকমক করচে-সোনা না কি দিয়ে বাঁধানো যেন। মন্দিরের চারিপাশে বাগান, চমৎকার গাছপালা, ফুল ফুটে আছে, অপূর্ব দেখতে–ঠিক যেন আমাদের সোনাদা চা-বাগানের ধারে বনের গাছের ডালে ডালে ফোঁটা নীল অর্কিডের ফুল! আর একদিন দেখেছিলাম ঠিক ওই জায়গায় বসেই আকাশ বেয়ে সন্ধ্যার সময় তিনটি সুন্দরী মেয়ে, পরনে যেন শ্বেতচমরীর লোমে বোনা সাদা চকচকে লুটিয়ে-পড়া কাপড়–তারা উড়ে যাচ্চে এক সারিতে, বোধ হয় পুরো পাঁচ মিনিট ধরে তাদের দেখেচি। তারপর রোদ চকচক করতে লাগল, আর তাদের স্পষ্ট দেখা গেল না–ওপরের দিকে যেতে যেতে মিলিয়ে গেল। এরকম নতুন নয়, কতবার দেখেছি, প্রায়ই দেখি, দু-পাঁচদিন অন্তর দেখি, দেখে দেখে আমার সয়ে গিয়েছে, আগের মত ভয় হয় না। কিন্তু এক-একবার ভাবি, এ আমার এক রকম রোগ–না, চোখ খারাপ হয়ে গিয়েছে, নাকি?
আমার কারুর সঙ্গে মিশতে সাহস হয় না এইজন্যে যে, হয়ত কোন সময় আবার অন্য ভাব এসে যাবে, আর কে সঙ্গে থাকবে সে আমায় ভাববে পাগল। হয়ত হাসবে, হয়ত লোককে বলে দেবে। এমনিও এ-বাড়িতে জ্যাঠাইমা, কাকীমা, কাকা, এঁরা আমায় পাগলই ভাবেন। কি করবো। আমি যা দেখি, ওঁরা তা দেখতে পান না, এই আমার অপরাধ। একটা উদাহরণ দিই–
ফাল্গুন মাসে ছোটকাকার মেয়ে পানী অসুখে পড়ল। একদিন দু’দিন গেল, অসুখ আর সারে না। জ্বর লেগেই আছে। সাতদিন কেটে গেল–জ্বর একই ভাব। দশ দিনের দিন। অসুখ এমনি বাড়ল, নৈহাটি থেকে বড় ডাক্তার আনবার কথা হ’ল।
পানীকে আমার এ-বাড়ির ছেলেমেয়েদের মধ্যে ভাল লাগে। তার বয়স বছর সাত আট, ঝাঁকড়া চুল মাথায়, চোখ কটা, সাহেবদের ছেলেমেয়েদের মত। এ-বাড়ির ছেলেমেয়েদের মুখে যেমন খারাপ কথা আর গালাগালি লেগেই আছে–পানীর কিন্তু তা নয়। তার একটা কারণ, সে এতদিন মামার বাড়িতে তার দিদিমার কাছে ছিল, গঙ্গার ওপারে ভদ্রেশ্বরে। সে বেশ মেয়ে, বেশ গান করতে পারে, প্রাণে তার দয়ামায়া আছে। পানীর অসুখ হয়ে পর্যন্ত আমার মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল–আমার ইচ্ছে হয়েছিল ওর কাছে গিয়ে বসে গায়ে হাত বুলিয়ে দিই–কিন্তু কাকীমা তো আমায় বিছানা ছুঁতে দেবে না, সেই ভয়ে পারতাম না।
পানীর তখন সতেরো দিন জ্বর চলচে–বুড়ো গোবিন্দ ডাক্তার ঘোড়ার গাড়ি করে স্টেশন থেকে এল––দালানে বসে মশলার কৌটো বার করে মশলা খেলে, ভাজা মশলার গন্ধে দালান ভুর ভুর করতে লাগল–চা ক’রে দেওয়া হ’ল, চা খেলে, তার পর ওষুধ লিখে দিয়ে ভিজিটের টাকা মেজকাকার হাত থেকে নিয়ে না-দেখেই পকেটে পুরলে–তার পর রোগীকে বার বার গরম জল খাওয়ানোর কথা বলে গাড়ি করে চলে গেল।
একটু একটু অন্ধকার হয়েছে কিন্তু এখনও বাড়িতে সন্ধ্যার শাঁখ বাজেনি, কি আলো জ্বালা হয়নি–হয়ত ডাক্তার আসবার জন্যে সকলে ব্যস্ত ছিল বলেই। আমি রোগীর ঘরে দোরের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম, কিন্তু পানীর বিছানায়–পানীর শিয়রে যে বসে আছে তাকে চিনতে পারলাম না। লালপাড় শাড়ী পরনে আধঘোমটা দেওয়া কে একজন, জ্যাঠাইমার মত দেখতে বটে কিন্তু জ্যাঠাইমা তো নয়! ঘরের মধ্যে আর কেউ নেই–এইমাত্র কাকীমা বাইরে গেছেন ডাক্তারে কি বলে গেল তাই জানতে ছোটকাকার কাছে। আমি ভাবচি লোকটা কে, এমন সময় তিনি মুখ তুলে আমার দিকে চেয়ে বললেন–জিতু, নির্মলাকে বোলো পানীকে আমি নিয়ে যাব, আমি ওকে ফেলে থাকতে পারবো না–ও আমার কাছ ভাল থাকবে, নির্মলা যেন দুঃখ না করে। আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম–কে নির্মলা আমি চিনি নে, যিনি বলছেন তিনিই বা কে, কোথা থেকে এসেছেন, কই এ বাড়িতে তো কোনদিন দেখিনি তাঁকে, পানীকে তিনি এই অসুস্থ শরীরে কোথায় নিয়ে যাবেন, এসব কথা ভাববার আগেই ছোটকাকীমা ঘরে ঢুকলেন–কিন্তু আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে বিছানার পাশে যিনি বসে আছেন, ছোট কাকীমা যে তাঁকে দেখতে পাচ্ছেন, এমন কোনো ভাব দেখলুম না।
বিছানায় যিনি বসে ছিলেন তিনি আমায় বললেন–জিতু, নির্মলাকে বল এইবার– আমি চলে যাচ্ছি।
আমি কিছু না ভেবে কলের পুতুলের মত চেয়ে বললাম–নির্মলা কে? ছোট কাকীমা আমার দিকে কট করে চেয়ে বললে,–কেন, সে খোঁজে কি দরকার? তিনি ভাবলেন আমি বুঝি তাঁকেই জিজ্ঞেস করচি। অন্য মহিলাটি বিছানা থেকে নেমে ওদিকের দরজা দিয়ে বার হয়ে চলে গেলেন, যাবার সময় আমাকে বললেন–এই তো নির্মলা ঘরে এসেচে।
আমি বললাম–আপনি কেন বলুন না নিজে?
ততক্ষণ তিনি বার হয়ে চলে গিয়েছেন।
ছোটকাকীমা আমার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে আছেন। বললেন–কি বকচিস পাগলের মত? ওদিকে চেয়ে কার সঙ্গে কথা বলচিস? নির্মলা কে সে খোঁজে তোমার কি দরকার শুনি?
জ্যাঠাইমা ঘরে ঢুকলেন সেই সময়ই। তিনি বললেন–কি হয়েছে? কি বলছে ও?
ছোটকাকীমা বললেন–আপন মনে কি বকচে দ্যাখো না দিদি–ও এ ঘর থেকে চলে যাক। আমার ভয় করে, ও ছেলের মাথার ঠিক নেই–আমার নাম করে কি বলচে।
জ্যাঠাইমা বললেন–কি বলছিলি কাকীমার নাম করে?
আমার বিস্ময় তখনো কাটেনি–আমি তখন কেমন হয়ে গিয়েচি। ছোটকাকীমার নাম যে নির্মলা আমি তা কখনও শুনিনি–ঐ মেয়েটি যে চলে গেল, আমার সঙ্গে কথা বলে গেল–ছোটকাকীমা তাঁকে দেখতে পেলেন না, তাঁর কথাও শুনতে পেলেন না এই বা কেমন! জ্যাঠাইমার কথার কোনো জবাব আমার মুখ দিয়ে বেরুলো না, আমার মাথা ঘুরে উঠল। তারপর কি যে ঘটল আমি তা জানি না।
জ্ঞান হলে দেখি মা আমার মাথা কোলে নিয়ে বসে কাঁদছেন। আমি দালানেই শুয়ে আছি। চারিপাশে বাড়ির অনেক মেয়ে জড় হয়েছে, সবাই বললে আমার মৃগীরোগ আছে। ভাবলাম হয়ত হবে, একেই বোধ হয় মৃগীরোগ বলে। আমার বড় ভয় হ’ল, বাবা মারা গিয়েচেন পাগল হয়ে, এ-বাড়ির অনেকের মুখে শুনেচি আমরাও পাগল হ’তে পারি। তার মধ্যে আমার নাকি পাগলের লক্ষণ আছে অনেক।
সে-সন্ধ্যার কথা কখনও ভুলব না। জীবনে এত ভয় আমার কোনদিন হয়নি–এই ভেবে ভয় হ’ল যে আমার সত্যিই কোনো কঠিন রোগ হয়েছে। কিন্তু কাউকে বলবার উপায় নেই রোগটা কি। মৃগীরোগই হয়ত হয়েছে, নয়তো বাবার মত পাগলই হয়ে যাব হয়ত–না, কি হবে!
যে রাত্রে বাবা পাগল হয়ে গিয়ে বালিশের তুলো ছিঁড়ে ঘরময় ছড়িয়ে দিলেন, কেরোসিনের টেমির মিটমিটে অস্পষ্ট আলোয় রাতদুপুরে তাঁর সেই অদ্ভুত সারা গায়ে, মুখে, মাথায় তুলোমাখা মূর্তি বার বার মনে আসতে লাগল–আমার মনে সে-রাত্রি, সে মূর্তি চিরদিনের জন্য আঁকা হয়ে আছে। ঐ রকম কি আমারও হবে!
মাকে আঁকড়ে ধরে শুয়ে রইলাম সারারাত। মনে মনে কতবার আকুল আগ্রহে প্রার্থনা করলাম–প্রভু যীশু, তুমি দেবতা, তুমি আমার এ রোগ সারিয়ে দাও, আমায় পাগল হ’তে দিও না। আমায় বাঁচাও।
সকালে একটু বেলায় রোদ উঠলে পানী মারা গেল।
জ্যাঠাইমা সকালে উঠে বৌদের কুটনো কুটবার উপদেশ দেবেন, কি কি রান্না হবে তা ঠিক করে দেবেন–এ বাড়িতে ভাগ্নে-বৌ ছাড়া কেউ গাই দুইতে পারে না–এদিকের কাজ সেরে জ্যাঠাইমা তাকে সঙ্গে নিয়ে গোয়ালে নিজের চোখের সামনে দুধ দোয়াবেন– সীতা বলে, পাছে ভাগ্নে-বৌ নিজের ছেলেমেয়েদের জন্যে কিছু সরিয়ে রাখে বোধ হয় এই ভয়ে। তারপর তিনি স্নান করে গরদের কাপড় পরে ঠাকুরঘরে ঢুকবেন–সেখানে আহ্নিক চলবে বেলা এগারোটা পর্যন্ত, সে-সময়ে ঠাকুরঘরের দোরে কারুর গিয়ে উঁকি দেবার পর্যন্ত হুকুম নেই। সবাই বলে জ্যাঠাইমা বড় পুণ্যবতী। পুণ্যবতীই তো! একদিন যে-ছবি দেখেছিলাম, ভুলিনি কোনদিন। জ্যাঠাইমা ঠাকুরঘর থেকে বার হয়ে এসে বারান্দায় দাঁড়িয়েচেন, পরনে গরদের শাড়ী, কপালে সিঁদুর, চন্দনের টিপ, টকটকে চেহারা–এমন সময় আমার মা একরাশ বাসি কাপড় নিয়ে গোবরছড়ার বালতি হাতে পুকুরের ঘাটে যাচ্চেন, পরনের ময়লা কাপড়ের জায়গায় কাদা গোবরের ছাপ, রুক্ষ চুল। বেলা বারোটার কম নয় সকাল থেকে মা’র মুখে এক ফোঁটা জল পড়েনি–
জ্যাঠাইমা ডেকে বললেন–বৌ, রান্নাঘরের ছোট জালার জল কি কাল তুমি তুলেছিলে? আমি না কতবার তোমায় বারণ করেচি ছোট জালায় তুমি জল ঢালবে না? বড় জালায় বেশী না পার তো তিন কলসী করে ঢেলেও তো বেগার শোধ দিলে পার?
ছোট জালার জল জ্যাঠামশায়, জ্যাঠাইমা বা কাকারা খান। জ্যাঠাইমার এ কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, মা গুরুমন্ত্র নেননি, মায়ের হাতের জল অতএব শুদ্ধ নয়, সে জল ওঁরা খাবেন কি করে?
সত্যিই তো জ্যাঠাইমা পুণ্যবতী। নইলে তিনি ঠাকুরঘরে পবিত্র দেহে পবিত্র মনে এতক্ষণ জপ-আহ্নিক করছিলেন, আর মা মরছিলেন বেলা বারোটা পর্যন্ত গোয়াল আঁস্তাকুড় ঘেঁটে– মা নাস্তিক মাতাল কেরানীর স্ত্রী, তার ওপর আবার মেমের কাছে লেখাপড়া শিখে জাত খুইয়েচেন, কেন ওঁরা জল খেতে যাবেন মা’র হাতের?
আমার মনে হ’ল ঠাকুরও শুধু বড়মানুষের, পুণ্যিও বড়মানুষের জন্যে–নইলে মায়ের, ভাগ্নেবৌয়ের, ভুবনের মায়ের সময় কোথায় তারা নিশ্চিন্ত মনে, শুচি হয়ে, গরদ পরে তাঁর পায়ে ফুলতুলসী দেবে?
বোধ হয় এই সব নানা কারণে জ্যাঠাইমাদের বাড়ির গৃহদেবতার প্রতি আমি অনেকটা চেষ্টা করেও কোনো ভক্তি আনতে পারতাম না। এক-একবার ভেবেচি হয়ত সেটা আমারই দোষ, আমার শিক্ষা হয়েছে অন্যভাবে, অন্য ধর্মাবলম্বী লোকেদের মধ্যে, তাদের কাছে যে দয়া-মমতা পেয়েছি, আর কোথাও তা পাইনি বলেই। ছেলেবেলা থেকে যীশুখৃষ্টের কথা পড়ে আসছি, তাঁর করুণার কথা শুনেচি, তাঁর কত ছবি দেখেচি। আমার কাছে একখানা ছবি আছে খৃস্টের, মেমেরা বড়দিনের সময় আমায় দিয়েছিল–বকের পালকের মত ধপধপে সাদা দীর্ঘ ঢিলে আলখাল্লা-পরা যীশু হাসি-হাসি মুখে দাঁড়িয়ে– চারিধারে তাঁর ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ভিড় করেছে, একটি ক্ষুদ্র শিশু তাঁর পা ধরে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করছে, আর তিনি তাকে ধরে তুলতে যাচ্ছেন নিচু হয়ে মুখে কি অপূর্ব জ্যোতি, কি সুন্দর চাউনি–আমি এ ছবিখানা বইয়ের ভেতরে রেখে দিই, রোজ একবার দেখি–এত ভালো লাগে!
কিন্তু যীশুখৃস্টের সম্বন্ধে কোনো ভাল বই পাইনে–আমার আরও জানবার ইচ্ছে হয় তাঁর কথা–মাকে যে মেমেরা পড়াত চা-বাগানে, তারা একখানা মথি-লিখিত সুসমাচার ও খানকতক ছাপানো কাগজ বিলি করেছিল, সেইগুলো কতবার পড়া হয়ে গিয়েছে, তা ছাড়া আর কোনো বই নেই। এখানে এসে পর্যন্ত আর কোনো নতুন বই আমার চোখে পড়েনি।
আমাদের স্কুলে একটা ছেলে নতুন এসে ভর্তি হয়েছে আমাদেরই ক্লাসে। তার নাম বনমালী, জাতে সদগোপ, রঙ খুব কালো, কিন্তু মুখের চেহারা বেশ, বয়সে আমার চেয়ে কিছু বড়। সে অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে, এখানে একটা ঘর ভাড়া করে থাকে, বামুনে রাঁধে। অনেক দূরের পাড়াগাঁয়ে তার বাড়ি, সেখানে লেখাপড়া শেখার কোনো সুবিধে নেই, তাই ওকে ওর বাপ-মা এই গাঁয়ে পাঠিয়েছে। কিন্তু লেখাপড়ার দিকে বনমালীর মন নেই, সে বাসার উঠোনে এক তুলসীচারা পুঁতে বাঁধিয়েচে, দিনরাত জপ করে, একবেলা খায়, মাছমাংস ছোঁয় না, শ্রীকৃষ্ণ নাম তার সামনে উচ্চারণ করবার জো নেই, তা হলেই তার চোখ দিয়ে জল পড়বে। রাত্রে জপের ব্যাঘাত হয় বলে বিকেলবেলা স্কুল থেকে গিয়ে খেয়েদেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বামুন ঠাকুরকে ছুটি দেয়–তার পর ব’সে ব’সে অনেক রাত পর্যন্ত জপ করে, হরিনাম করে। সে সময় কেউ কাছে গেলে সে ভারি চটে। অদ্ভুত ধরনের ছেলে বলে তাকে সকলে ভারি খেপায়–স্কুলের ছেলেরা তার সামনে কিষ্ট কিষ্ট বলে চেঁচায় তার চোখে জল বেরোয় কি না দেখবার জন্যে, ওই নিয়ে মাস্টারেরা পর্যন্ত খিঁচুনি দিতে বাকী রাখে না। সেদিন তো এ্যালজেব্রার আঁক না পারার দরুন আমাদের সামনে সেকেন্ড মাস্টার ওকে বললে–তুমি তো শুনিচি কেষ্ট নাম শুনলে কেঁদে ফেল–তা যাও, পয়সা আছে বাপের, মঠ বানাও, মচ্ছব দেও, লেখাপড়া করবার শখ কেন? এ-সব তোমার হবে না বাপু।
আমি একদিন বনমালীর কাছে সন্ধ্যার সময় গিয়েছি। ও তখন একটা টুলের ওপর ব’সে একমনে দেওয়ালের দিকে চেয়ে বোধ হয় জপ করচে–আমায় দেখে উঠে দোর খুলে দিল, হেসে বসতে বললে। ওকে অদ্ভুত মনে হয়, সেজন্যেই দেখা করতে গিয়েছিলাম যে তা নয়–আমার মনে হয়েছিল ও যে-রকম ছেলে, ও বোধ হয় আমার নিজের ব্যাপারগুলোর একটা মীমাংসা করে দিতে পারবে। তা ছাড়া ওকে আমার ভাল লাগে খুব, ওকে ভাল মানুষ পেয়ে সবাই খেপায়, অথচ ও প্রতিবাদ করে না, অনেক সময় বোঝে না যে তারা খেপাচ্ছে, এতে আমার বড় মায়া হয় ওর ওপর।
বনমালীকে জিজ্ঞেস করলাম সে কিছু দেখে কিনা। সে আমার কথা বুঝতে পারলে না, বললে–কি দেখবো?
তাকে বুঝিয়ে বললাম। না,–সে কিছু দেখে না।
তারপর একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। ঘরে একখানা ছবি ছিল, আমি সেদিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললাম–ওখানা কি তোমার ঠাকুরের ছবি?
বনমালীর গলার সুর বদলে গেল, চোখের চাউনি অন্য রকম হয়ে গেল। সে বললে– ঠিক বলেচ ভাই, আমার ঠাকুরের ছবি, চমৎকার কথা বলেচ ভাই–ওই তো আমার সব, আমার ঠাকুর শুধু কেন, তোমার ঠাকুর সবারই ঠাকুর—
বলতে বলতে দর দর করে তার চোখে জল পড়তে লাগল।
আমি অবাক হয়ে গেলাম। কিন্তু একটু পরে বনমালীর কান্নার বেগ থামলে গর্বের সুরে বললাম–খুব গোপনীয় কথা বললাম ওকে–কারও কাছে এ পর্যন্ত মুখ ফুটে কথাটা বলিনি। বললাম–আমার ঠাকুর অন্য কেউ নয়, আমার ঠাকুর যীশুখ্রীস্ট–আমার কাছেও ছবি আছে–
বনমালী হাঁ করে আমার দিকে চেয়ে রইল–তারপর অপ্রতিভভাবে বললে–ও, তোমরা খৃস্টান?
আমি চুপ করে রইলাম।
বনমালী ভেবে বললে–তাঁর কাছে সব সমান—
আমি বললাম–কার কাছে?
–শ্রীহরির কাছে ভাই, আবার কার কাছে? তাঁর কাছে কি আর হিন্দু, মোছলমান, খৃস্টান আছে? তিনি যে পতিতপাবন–অধমের ঠাকুর–
আমার মনে ব্যথা লাগল এই ভেবে, বনমালী আমাকে অধম মনে করছে। যীশুখৃস্টকে ও ছোট করতে চায়। আমি বললাম–যীশুর কাছেও সব সমান। পাপীদের জন্যে তিনি প্রাণ দিয়েছিলেন–জান? মথিলিখিত সুসমাচারে লিখেছে, যে তাহাতে বিশ্বাস করে সে অনন্ত জীবন–
মথি-লিখিত সুসমাচারের বাইরে আমার আর কিছু জানা নেই। বনমালী কিন্তু সংস্কৃতে শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান আবৃত্তি করে আমায় শ্রীকৃষ্ণের রূপ বুঝিয়ে দিলে–আরও অনেক কথা বললে। আমি দু-তিন দিন তার কাছে গেলাম, তার ঠাকুর সম্বন্ধে শুনবার জন্যে।
জ্যাঠাইমাদের বাড়ির সকলের চেয়ে ও বেশী জানে ওদের ধর্ম সম্বন্ধে–এ আমার মনে হ’ল। কিন্তু বনমালী আমার খ্রীস্টভক্তি ভাল চোখে দেখলে না, বললে–হিন্দু হয়ে ভাই এ তোমার ভারি অদ্ভুত কাণ্ড যে তুমি অপরের দেবতাকে ভক্তি করো। গীতায় বলেছে, স্বধর্মে নিধনং শেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ—-অর্থাৎ নিজের ধর্মে–
আমি তাকে বুঝিয়ে বললাম, হিন্দু আমি কখনই না। আমরা যেখানে যে-অবস্থায় মানুষ হয়েচি সেখানে হিন্দুধর্মের কথা কিছু শুনিনি কোনো দিন কেউ বলত না। যা বলত, তাই শুনেচি, তাই বিশ্বাস করেছি–তা মনে লেগেছে। এতে আমার কি কোনো দোষ হয়েছে ভাই?
সেদিন সন্ধ্যার সময় আমাদের দালানে আমি বসে পড়চি, এমন সময় কার পায়ের শব্দ শুনে চেয়ে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলাম–ছোটকাকীমা দাঁড়িয়ে! ছোটকাকীমা বড় মানুষের মেয়ে, তিনি তো কস্মিনকালে আমাদের ভাঙা দালানে পা দেননি–বিশেষ করে আমাদের দু-চোখে তিনি দেখতে পারেন না কোনো কালে–বরং মেজকাকীমা সময়ে অসময়ে নরম হন, ছোট কাকীমার মুখে মিষ্টি কথা কোনো দিন শুনিওনি। আমাদের ঘরে আর কেউ নেই–দাদা এখনও ফেরেনি–সীতা ও মা জ্যাঠাইমাদের অন্দরে। আমি দাঁড়িয়ে উঠে থতমত খেয়ে বললাম–কি কাকীমা?
ছোটকাকীমা এদিক-ওদিক চেয়ে নীচু সুরে বললেন–তোর সঙ্গে কথা আছে জিতু।
আমি বললাম–কি বলুন?
কাকীমা বললেন–পানী যে-রাতে মারা যায়, সেদিন তুই আমায় কি বলেছিলি মনে আছে?
আমার ভয় হ’ল, বললাম–না কাকীমা।
ছোটকাকীমা হঠাৎ আমার হাত দুটো তাঁর দু’হাতের মধ্যে নিয়ে বললেন–বল বাবা জিতু, সেদিন তোর কথা সবাই উড়িয়ে দিয়েছিল, আমি কিন্তু তারপর সব বুঝেছিলাম, কাউকে বলিনি। পানী ছেড়ে গিয়ে আমায় পাগল করে রেখে গিয়েচে–তুই বল জিতু। আমার মাকে তুই দেখেছিলি সে-রাত্রে, তিনি পানীকে ভালবাসতেন, তাই নিতে এসেছিলেন-মরে গিয়েও তাঁর পানীর কথা—
আমি জানতাম না যে পানীর দিদিমা মারা গিয়েছেন। আমি বিস্ময়ের সুরে জিজ্ঞেস করলাম–আপনার মা বেঁচে নেই?
–না, পানী তাঁর কাছ থেকে ফাল্গুন মাসে এল, তিনি আষাঢ় মাসে তো মারা গেলেন। তুই পানীকে দেখতে পাস জিতু? তোকে সেদিন সবাই পাগল বললে, কিন্তু আমি তারপর ভেবে দেখলাম তোর কথার একটুও পাগলামি নয়–সব সত্যি। তুই আমার মাকে দেখতে পেয়েছিলি–সত্যি বল না জিতু বাবা পানীকে দেখিস?
আমার চোখেও জল এল। ছোট কাকীমাকে এত কাতর দেখিনি কখনও–তাছাড়া পানীকে আমিও বড় ভালবাসতাম এ বাড়ির ছেলেমেয়েদের মধ্যে। বললাম–না কাকীমা, পানীকে আমি কোনো দিন দেখিনি–আপনার পা ছুঁয়ে বলতে পারি–
ছোটকাকীমা আরও কি বলতে যাচ্ছিলেন, মেজকাকার গলার স্বর শুনে তিনি পালিয়ে পেলেন। ছোটকাকীমার কথা শুনে আমি কিন্তু আকাশ-পাতাল ভাবতে বসলাম। আমি সেদিন সত্যিসত্যি কাউকে দেখেছিলাম? তবে? সে যেই হোক, পানীর দিদিমাই হোক, মরাই হোক বা জীবন্তই হোক! এটা তা হলে আমার রোগ নয়? আর কেউ তবে দেখে না কেন?
কিংবা হয়ত ছোটকাকীমা মেয়ের শোকে বুদ্ধি হারিয়েছেন, কি বলচেন না-বলচেন, উনিই জানেন না। ওঁর কথার উপর বিশ্বাস কি?
.
০৬.
জ্যাঠামশায়দের বাড়ি আরও বছর দুই কেটে গেল এই ভাবেই। যত বছর কেটে যায়, এদের এখানে থাকা আমার পক্ষে তত বেশি কঠিন হয়ে পড়তে লাগল। আমার বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেক জিনিস আমি বুঝতে পারি আজকাল, আগে আগে অত বুঝতাম না। এ বাড়িতে থাকা আমার পক্ষে আরও কঠিন হয়ে উঠেছিল এইজন্যে যে, আমি চেষ্টা করেও জ্যাঠাইমাদের ধর্ম ও আচারের সঙ্গে নিজেকে কিছুতেই খাপ খাওয়াতে পেরে উঠলাম না।
এঁরা খুব ঘটা ক’রে যেটা ধর্ম বলে আচরণ করেন, আমার মনের সঙ্গে সেটা তো আদৌ মেলে না–আমি মনে যা বলি, বাইরে তা করি–কিন্তু ওঁরা তাতে চটেন। ওঁদের ধর্মের যেটা আমার ভাল লাগে–সেটাকে ওঁরা ধর্ম বলেন না।
কিন্তু একটা ব্যাপার হয়েছে এই, আগে ভাবতাম শুধু জ্যাঠাইমাদের বাড়িতেই বুঝি এই রকম, এখন বয়স বাড়বার সঙ্গে বুঝতে পেরেছি–এ গ্রামের অধিকাংশই এই রকম– জ্যাঠাইমায়েরা একটু বেশী মাত্র।
এতেই আমার সন্দেহ হ’ল বোধ হয় আমার মধ্যেই কোনো দোষ আছে, যার ফলে আমি এঁদের শিক্ষা নিতে পারচি নে। ভাবলাম আমার যে ভাল লাগে না, সে বোধ হয় আমি বুঝতে পারি না বলেই হয়ত চা-বাগানে থাকার দরুন ওদের ধর্ম আমরা শেখবার সুযোগ পাইনি, যে আবহাওয়ার মধ্যে ছেলেবেলা থেকে মানুষ হয়েছি, সেটাই এখন ভাল লাগে।
ম্যাট্রিক পাস করে শ্রীরামপুর কলেজে ভর্তি হলাম। জ্যাঠামশায়দের গ্রাম আটঘরার নবীন চৌধুরী–যার বড় ছেলে ননী ভাল ফুটবল খেলতে পারে এবং যে প্রায়শ্চিত্তের বাধাবিঘ্ন না মেনে বাবার সৎকারের সময়ে দলবল জুটিয়ে এনেছিল–তারই ভগ্নীপতির বাড়ি অর্থাৎ নবীন চৌধুরীর বড় মেয়ে শৈলবালার শ্বশুরবাড়ি শ্রীরামপুরে। ননীর যোগাড়যন্ত্রে তাদের শ্বশুরবাড়িতে আমার থাকবার ব্যবস্থা হ’ল।
এসে দেখি এদেরও বেশ বড় সংসার, অনেক লোক। শৈলদিদির স্বামীরা ছ’ভাই, তার মধ্যে চার ভাইয়ের বিয়ে হয়েছে, আর একটি আমার বয়েসী, ফার্স্ট ইয়ারেই ভর্তি হ’ল আমার সঙ্গে। সকলের ছোট ভাই স্কুলে পড়ে। শৈলদি বাড়ির বড়বৌ আমি তাঁর দেশের লোক, সবাই আমাকে খুব আদরযত্ন করলে। এখানে কিছুদিন থাকবার পরে বুঝলাম যে, সংসারে সবাই জ্যাঠামশায়দের বাড়ির ছাঁচে গড়া নয়। চা-বাগান থেকে এসে বাংলাদেশ সম্বন্ধে যে একটা হীন ধারণা আমার হয়েছিল, সেটা এখানে দু-চার মাস থাকতে থাকতে চলে গেল। আর একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম যে এ বাড়ির মেয়েরা কেউ কারও বড় একটা অধীন নয়। কোনো একজনকে সকলের ভয় করে চলতে হয় না বা কোনো একজনের কথায় সকলকে উঠতে বসতে হয় না।
আমি থাকি বাইরের একটা ঘরে, কিন্তু অল্পদিনেই আমি বাড়ির ছেলে হয়ে পড়লাম। শৈলদিদি খুব ভাল, আমাকে ভাইয়ের মত দেখে। কিন্তু এতবড় সংসারের কাজকর্ম নিয়ে সে বড় ব্যস্ত থাকে–সব সময় দেখাশুনো করতে পারে না। শৈলদিদির বয়স আমার মেজকাকীমার চেয়ে কিছু ছোট হবে–তিন-চারটি ছেলেমেয়ের মা। আটঘরায় থাকতে খুব বেশী আলাপ ছিল না, দু-একবার জ্যাঠামশায়দের বাড়ি বেড়াতে গিয়ে মায়ের সঙ্গে আলাপ করে এসেছিল, তারপর ননী কথাটা পাড়তেই তখনি রাজী হয়ে যায় আমার এখানে রাখবার সম্বন্ধে। শৈলদিদির স্বামী তার কোনো কথা ফেলতে পারে না।
বাড়ির সকলের সঙ্গে খুব আলাপ হয়ে গেল। বাড়ির মধ্যে সর্বত্র যাই–জ্যাঠামশায়দের বাড়ির মত এটা ছুঁয়ো না, ওটা ছুঁয়ো না–কেউ করে না। সব ঘরে যাই, সব বিছানাতেই বসি–সবাই আদরযত্ন করে, পছন্দ করে। এখন বয়স হয়েচে বুঝতে পেরেচি, আটঘরায় যতটা বাঁধাবাঁধি, এসব শহর-বাজারে অত নেই এদের। কষ্ট হয় মার জন্যে, সীতার জন্যে–তারা এখনও জ্যাঠাইমার কঠিন শাসনের বাঁধনে আবদ্ধ হয়ে ক্রীতদাসীর মত উদয়াস্ত খাটচে। দাদার জন্যেও কষ্ট হয়। সে লেখাপড়া শিখলে না–চাকুরি করবে, সংসারের দুঃখ ঘুচোবে বলে–কিন্তু চাকুরি পায় না, ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, আজ বারো টাকা মাইনের চাকুরি করে, কাল জবাব হয়ে যায়, আবার আর এক জায়গায় ষোল টাকা মাইনের চাকুরি জোটায়। এত সামান্য মাইনেতে বিদেশে খেয়ে পরে কোন মাসে পাঁচ টাকা, কোন মাসে তিন টাকার বেশী মাকে পাঠাতে পারে না, তাতে কি দুঃখ ঘুচবে?
অথচ না শিখলে লেখাপড়া, না করতে পারলে কিছু।
কলেজের ছুটির পরে গঙ্গার ধারে একখানা বেঞ্চির ওপর বসে এই সব কথাই ভাবছিলাম। মাঝে মাঝে ভয়ানক ইচ্ছে হয় আবার একবার চা-বাগানের দিকে যাই, আর একবার হিমালয় দেখি। কতকাল রডোডেনড্রন ফুল দেখিনি, পাইন-বন দেখিনি, কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখিনি–সে রকম শীত আর পাইনি কোনোদিন,–এদের সবাইকে দেখাতে ইচ্ছে হয় সে দেশ। স্কুলে যখন প্রবন্ধ লিখতে দিত, আমি হিমালয় নিয়ে লিখতাম– আমার লেখা সকলের চেয়ে ভাল হ’ত–কারণ বাল্যের স্বপ্ন-মাখানো সে ওক পাইন বন, ঝর্ণা, তুষারমণ্ডিত কাঞ্চনজঙ্ঘা, কুয়াশা, মেঘ আমার কাছে পুরনো হবে না কোনো দিন, তাদের কথা লিখতে গেলে নতুন ভাব ও ভাষা কোথা থেকে এসে জোটে, মনে হয় আরও লিখি, এখনও সব বলা হয়নি। লেখা অপরে ভাল বললেও আমার মন তৃপ্ত হ’ত না, মনে হ’ত যা দেখেছি তার অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশও আঁকতে পারলাম না–অপরে ভাল বললে কি হবে, তারা তো আর দেখেনি?
ওপারে ব্যারাকপুরের সাদা বাড়িগুলো যেন সবুজের সমুদ্রে ডুবে আছে। ঠিক যেন চা ঝোপের আড়ালে ম্যানেজার সাহেবের কুঠী–লাল টালির ছাদ থাকলেই একেবারে চা বাগান। ওই দিকে চেয়েই তো রোজ বিকেলে আমার মনে হয় বাল্যের চা-বাগানের সেই দিনগুলো।
বাড়ি ফিরে গেলাম সন্ধ্যার পরে। চাকরকে ডেকে বললাম, লুলু আলো দিয়ে যা। এমন সময়ে ভবেশ এল। ভবেশ সেকেন্ড ইয়ারে পড়ে, খুব বুদ্ধিমান ছেলে, স্কলারশিপ নিয়ে পাস করেচে–প্রথম দিনেই কলেজে এর সঙ্গে আলাপ হয়।
ভবেশের দৈনন্দিন কাজ–রোজ এসে আমার কাছে খৃস্টান ধর্মের নিন্দা করা। আমাকে ও খৃস্টান ধর্মের কবল থেকে উদ্ধার করে নাকি হিন্দু করবেই। আজও সে আরম্ভ করলে বাইবেলটা নিতান্ত বাজে, আজগুবী গল্প। খৃস্টান ইউরোপ এই সেদিনও রক্তে সারা দুনিয়া ভাসিয়ে দিলে গ্রেট ওয়ারে। কিসে তুমি ভুলেচ? রোজ যাও পিকারিং সাহেবের কাছে ধর্মের উপদেশ নিতে। ওরা তো তোমাকে খৃস্টান করতে পারলে বাঁচে। তা ছাড়া আজ হিন্দুদের বলবৃদ্ধি করা আমাদের সবার কর্তব্য–এটা কি তোমার মনে হয় না?
আমি বললাম–তুমি ভুল বুঝেচ ভবেশ, তোমাকে এক দিনও বোঝাতে পারলাম না যে আমি খৃস্টান নই খৃস্টান ধর্ম কি জিনিস আমি জানিনে–জানবার কৌতূহল হয় তাই পিকারিং সাহেবের কাছে জানতে চাই। আমি যীশুখৃষ্ট্রের ভক্ত, তাঁকে আমি মহাপুরুষ বলে মনে করি। তাঁর কথা আমার শুনতে ভাল লাগে। তাঁর জীবন আমাকে মুগ্ধ করে। এতে দোষ কিসের আমি তো বুঝি নে।
–ও বটে! বুদ্ধ, চৈতন্য, কৃষ্ণ, রামকৃষ্ণ, এঁরা সব ভেসে গেলেন–যীশুখৃস্ট হ’ল তোমার দেবতা! এঁরা কিসে ছোট তোমার যীশুর কাছে জিজ্ঞেস করি?
–কে বলেছে তাঁরা ছোট? ছোট কি বড় সে কথা তো উঠচে না এখানে? আমি তাঁদের কথা বেশী জানি নে। যতটুকু জানি তাতে তাঁদের শ্রদ্ধা করি। কিন্তু এও তো হয়, কেউ একজনকে বেশি ভালবাসে আর একজনকে কম ভালবাসে?
–তুমি যতই বোঝাও জিতেন, আমার ও ভাল লাগে না। দেশের মাটির সঙ্গে যোগ নেই ওর। তোমার মত চমৎকার ছেলে যে কেন বিপথে পা দিলে ভেবে ঠিক করতে পারিনে। তোমার লজ্জা করে না একথা বলতে যে, রামকৃষ্ণ, বুদ্ধ, চৈতন্যের কথা কিছু জান না, তাঁদের কথা জানতে আগ্রহও দেখাও না, অথচ রোজ যাও যীশুখৃস্টের বিষয় শুনতে? একশোবার বলবো তুমি বিপথে পা দিয়ে দাঁড়িয়েচ। কই, একদিন গীতা পড়েচ? অথচ গসপেল পড়তে যাও পিকারিঙের কাছে–তোমাকে বন্ধু বলি তাই কষ্ট হয়, নইলে তুমি উচ্ছন্ন যাও না, আমি বলতে যাব কেন?
ভবেশ চলে গেলে অনেক রাত পর্যন্ত কথাটা ভাবলাম। খৃস্টকে আমি ভক্তি করি, খৃস্টের কথা বলতে ভাল লাগে, শুনতে ভাল লাগে। এতে দোষ আছে কিছু? মহাপুরুষের কি দেশ-বিদেশ আছে?
রাত্রে বাড়ির মধ্যে খেতে গিয়ে দেখি আর সকলের খাওয়া হয়ে গিয়েচে। ছোট বউ অর্থাৎ শৈলদিদি ছোট জায়ের রান্নার পালা ছিল এবেলা–তিনি হাঁড়িকুড়ি নিয়ে বসে আছেন। আমি খেতে বসলাম কিন্তু কেমন অস্বস্তি বোধ হ’তে লাগল–শৈলদিদির এই ছোট জাকে আমি কি জানি কেন পছন্দ করিনে। মেজবউ, সেজবউকে যেমন মেজদি, সেজদি বলে ডাকি–ছোটবউকে আমি এ পর্যন্ত কোন কিছু বলে ডাকিনি। অথচ তিনি আমার সামনে বেরোন বা আমার সঙ্গে কথা বলেন। ছোটবউয়ের বয়স আমার সমান হবে, এই সতেরো আঠারো–আমি যদিও ‘আপনি’ বলে কথা বলি। বাড়ির সব মেয়েরা ও বৌয়েরা জানে যে ছোটবউয়ের সঙ্গে আমার তেমন সদ্ভাব নেই। কেন আমি তাঁকে ছোটদিদি বলে ডাকিনে, শৈলদি আমায় এ নিয়ে কতবার বলেছে। কিন্তু আমার যা ভাল লাগে না, তা আমি কখনও করিনে।
সেদিন এক ব্যাপার হয়েছে। খেয়ে উঠে অভ্যাসমত পান চেয়েচি–কাউকে বিশেষ করে সম্বোধন করে নয়, যেন দেওয়ালকে বলচি এই ভাবে। ছোটবউ আধ-ঘোমটা দিয়ে এসে পান আমার হাতে দিতে গেলেন–আমার কেমন একটা অস্বস্তি বোধ হ’ল কেন জানিনে, অন্য কারুর বেলা আমার তো এমনি অস্বস্তি বোধ হয় না? পান দেবার সময় তাঁর আঙুলটা আমার হাতে সামান্য ঠেকে গেল–আমি তাড়াতাড়ি হাত টেনে নিলাম। আমার সারা গা কেমন শিউরে উঠল, লজ্জা ও অস্বস্তিতে মনে হ’ল, পান আর কখনও এমনভাবে চাইব না। মেজদি কি শৈলদির কাছে গিয়ে চেয়ে নেবো।
সেইদিন থেকে ছোটবউকে আমি এড়িয়ে চলি।
মাস কয়েক কেটে গেল। শীত পড়ে গিয়েছে।
আমি দোতলার ছাদে একটা নিরিবিলি জায়গায় রোদে পিঠ দিয়ে বসে জ্যামিতির আঁক কষচি।
সেজদি হাসতে হাসতে ছাদে এসে বললেন–জিতু এস, তোমায় ওরা ডাকছে।
আমি বললুম–কে ডাকচে সেজদি?
সেজদির মুখ দেখে মনে হ’ল একটা কি মজা আছে। উৎসাহ ও কৌতূহলের সঙ্গে পেছনে পেছনে গেলাম। দোতলার ওদিকের বারান্দাতে সব মেয়েরা জড়ো হয়ে হাসাহাসি করছে। আমায় সবাই এসে ঘিরে দাঁড়াল, বললে–এস ঘরের মধ্যে।
তাদের পেছনে ঘরে ঢুকতেই সেজদি বিছানার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন–ওই লেপটা তোল তো দেখি কেমন বাহাদুরি।
বিছানাটার উপর আগাগোড়া লেপ-ঢাকা কে একজন শুয়ে আছে লেপমুড়ি দিয়ে। সবাই বললে–তোল তো লেপটা!
আমি হাসিমুখে বললাম–কি বলুন না সেজদি, কি হয়েচে কি?
ভাবলুম বোধ হয় শৈলদির ছোট দেওর অজয়কে এরা একটা কিছু সাজিয়েচে বা ঐ রকম কিছু। তাড়াতাড়ি লেপটা টেনে নিয়েই চমকে উঠলাম। লেপের তলায় ছোটবৌঠাকরুন, মুখে হাসি টিপে চোখ বুজে শুয়ে।
সবাই খিল খিল করে হেসে উঠল। আমি লজ্জায় লাল হয়ে তাড়াতাড়ি ঘরের বার হয়ে গেলাম। বারে, এ কি কাণ্ড ওদের? কেন আমায় নিয়ে এ রকম করা? তা ছাড়া– ছিঃ–না, ওকি কাণ্ড! ছোটবৌঠাকরুন স্বেচ্ছায় এ ষড়যন্ত্রের মধ্যে আছেন নিশ্চয়। আমার রাগ হ’ল তাঁর ওপরে।
এর দিন-দুই পরে আমি আমার নিজের ঘরে একা বসে আছি, এমন সময় হঠাৎ ছোট-বৌঠাকরুনকে দোরের কাছে দেখে অবাক হয়ে গেলাম–তিনি আমার ঘরে কখনও আসেননি এ পর্যন্ত। কিন্তু তিনি যেমনি এলেন, তেমনি চলে গেলেন, একটু দাঁড়ালেন না, যাবার আগে ঘরের মধ্যে কি একটা ফেলে দিয়ে গেলেন।
আমি বিস্মিত হয়ে তুলে দেখলাম একখানা ভাঁজ করা ছোট কাগজ–একখানা চিঠি! ছোট্ট চিঠি, দু-কথায়–
সেদিন যা করে ফেলেচি, সেজন্য আপনার কাছে মাপ চাই। আমি নিজের ইচ্ছেতে কিছু করিনি। দলে পড়ে করেচি, কদিন ধরে ভাবচি আপনার কাছে মাপ চাইব–কিন্তু লজ্জায় পারিনি! আমি জানি আপনার মন অনেক বড়, আপনি ক্ষমা করবেন।
পত্রে কোন নাম নেই। আমি সেখানা বার বার পড়লাম–তারপর টুকরো টুকরো ক’রে ছিঁড়ে ফেললাম–কিন্তু টুকরোগুলো ফেলে দিতে গিয়ে কি ভেবে আমার একটা ছোট মানিব্যাগ ছিল, তার মধ্যে রেখে দিলাম।
সেদিন থেকে আমার কি হ’ল, আমি একা থাকলেই ছোটবৌঠাকরুনের কথা ভাবি। কিছুতেই মন থেকে আমি তাঁর চিন্তা ছাড়তে পারিনে। দু-পাঁচদিন করে হপ্তাখানেক কেটে গেল। আমি বাড়ির মধ্যে তেমন আর যাইনে–অত্যন্ত ভয়, পাছে একা আছি এমন অবস্থায় ছোটবৌঠাকরুনের সঙ্গে দেখা হয়ে পড়ে। ছোটবৌয়ের রান্নার পালার দিন আমি সকাল সকাল খেয়ে নি, যখন অনেকলোক রান্নাঘরে থাকে। যা যখন দরকার হয়, শৈলদি কি সেজদির কাছে চাই–ওদের গলা না শুনতে পেলে বাড়ির মধ্যে যেতে সাহস হয় না।
সেজদি একদিন বললেন–জিতু, তুমি কলেজ থেকে এসে খাবার খাওয়া ছেড়ে দিলে নাকি? বিকেলে তো বাড়ির মধ্যে থাকই না, আসই না, কোথাও থেকে খেয়ে আস বুঝি?
আমি জানি বিকেলের চা-খাবার প্রায়ই ছোটবৌ তৈরি করেন–আর সে সময় বড় একটা কেউ সেখানে থাকে না। যে যার খেয়ে চলে যায়। ইচ্ছা করেই বিকেলে চা খেতে যাই নে। পয়সা যেদিন থাকে, স্টেশনের দোকান থেকে খেয়ে আসি।
শীত কেটে গেল, বসন্ত যায়-যায়। আমার ঘরে জানলার ধারে বসে পড়চি, হঠাৎ জানলার পাশের দরজা দিয়ে ছোটবৌঠাকরুন কোথা থেকে বেরিয়ে এসে বাড়ি ঢুকচেন, সঙ্গে শৈলদির ছেলে কালো। তিনি আমায় দেখতে পাননি। আমি অপলকে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলাম তাঁর দিকে। তাঁকে যেন নতুনরূপে দেখলাম–আরো কতবার দেখেছি, কিন্তু আজ দেখে মনে হ’ল এ-চোখে আর কখনও দেখিনি তাঁকে। তাঁর কপালের অমন সুন্দর গড়ন, পাশের দিক থেকে তাঁর মুখ যে অমন সুশ্রী দেখায়, ভুরুর ও চোখের অমন ভঙ্গি– এ-সব আগে তো লক্ষ্য করিনি। যখন কেউ দেখে না, তখন তাঁর মুখের কি অদ্ভুত ধরনের ভাব হয়! তিনি বাড়ির মধ্যে ঢুকে যেতেই আমার চমক ভাঙলো। বই খুলে রেখে দিলাম–পড়ায় আর মন বসল না, সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক হয়ে গেলাম। কি একটা কষ্ট হ’তে লাগল বুকের মধ্যে–যেন নিশ্বাস-প্রশ্বাস আটকে আসচে। মনে হ’ল চুপ করে বসে থাকতে পারব না, এক্ষুনি ছুটে মুক্ত বাতাসে বেরুতে হবে।
সেই রাত্রে আমি তাঁকে চিঠি লিখতে বসলাম–চিঠি লিখে ছিঁড়ে ফেললাম। আবার লিখে আবার ছিড়লাম। সেদিন থেকে তাঁকে উদ্দেশ্য করে চিঠি লেখা যেন আমার কলেজের টাস্কের সামিল হয়ে দাঁড়ালো–কিন্তু লিখি আর ছিঁড়ে ফেলি।
দিন-পনের পরে ঠিক করলাম, আজ চিঠি দেবই। সেদিন বেলা দেড়টার মধ্যে কলেজ থেকে ফিরে এলাম–গ্রীষ্মের দুপুর, সবাই ঘুমুচ্চে। আমি বাড়ির মধ্যে ঢুকলাম, সিঁড়ির পাশে দোতলায় তাঁর ঘর, তিনি ঘরে বসে সেলাই করছিলেন–আমি সাহস করে ঘরে ঢুকে চিঠি দিতে পারলাম না, চলে আসছিলাম, এমন সময় তিনি মুখ তুলেই আমায় দেখতে পেলেন, আমি লজ্জায় ও ভয়ে অভিভূত হয়ে সেখান থেকে সরে গেলাম, ছুটে নীচে এলাম–পত্র দেওয়া হ’ল না, সাহসই হ’ল না। বাড়ি থেকে বেরিয়ে পথে পথে উদভ্রান্তের মত ঘুরে বেড়ালাম লক্ষ্যহীন ভাবে। সারাদিন ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে অনেক রাত্রে বাড়ি যখন ফিরি, রাত তখন বারোটা। বাড়িতে আবার সেদিন লক্ষ্মীপূজা ছিল। খেতে গিয়ে দেখি রান্নাঘরের সামনের বারান্দায় আমার খাবার ঢাকা আছে, শৈলদি ঢুলচেন রান্নাঘরের চৌকাঠে বসে। মনে মনে অনুতাপ হ’ল, সারা বিকেল খাটুনির পরে শৈলদি বেচারী কোথায় একটু ঘুমুবে, আর আমি কি-না এভাবে বসিয়ে রেখেচি!
আমাকে দেখে শৈলদি বললে—-বেশ, কোথায় ছিলি এতক্ষণ?
কথার উত্তর দিতে গেলে মুশকিল, চুপচাপ খেতে বসলাম–শৈলদি বললে–না খেয়ে ঢন ঢন করে বেড়িয়ে বেড়িয়ে কণ্ঠার হাড় বেরিয়ে গিয়েচে। চা খেতেও আসিস নে বাড়ির মধ্যে, কালোকে দিয়ে বাইরের ঘরে খাবার পাঠিয়ে দিলেও পাওয়া যায় না–থাকিস কোথায়?
খানিকক্ষণ পরে পাতের দিকে চেয়ে বললে–ও কি, ভাল করে ভাত মাখ। ঐ ক’টি খেয়ে মানুষ বাঁচে ভাই? তোরা এখন ছেলেমানুষ, খাবার বয়স। লুচি আছে ভোগের, দেবো? পায়েস তুই ভালবাসিস, এক বাটি পায়েস আলাদা করা আছে। কই মাছের মুড়ো ফেললি কেন, চুষে চুষে খা। আহা, কি ছিরি হচ্ছে চেহারার!
পরদিন কিসের ছুটি। আমি দোতলার ছাদে কালোকে ডাকতে গিয়েছি তার প্রাইভেট টিউটর নীচে পড়াতে এসেচে বলে। সন্ধ্যার অন্ধকার হয়েছে। ওপরে উঠেই আমি একেবারে ছোটবৌঠাকরুনের সামনে পড়ে গেলাম। তাঁর কোলে মেজদির দেড় বছরের খুকী মিন্টু–সে খুব ফুটফুটে ফর্সা বলে বাড়ির সকলের প্রিয়, সবাই তাকে কোলে পাবার জন্যে ব্যগ্র। ছোটবৌঠাকরুন হঠাৎ আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন খুকীকে কোলে করে। আমি বিস্মিত হ’লাম, কপালে ঘাম দেখা দিল। খুকী আমায় চেনে, সে আমার কোলে ঝাঁপিয়ে আসতে চায়। ছোটবৌঠাকরুন আমার আরও কাছে এগিয়ে এসে দাঁড়ালেন– খুকীকে আমার কোলে দিলেন। তাঁর পায়ের আঙুল আমার পায়ের আঙুলে ঠেকল। আমি তখন লাল হয়ে উঠেচি, শরীর যেন ঝিম ঝিম করচে। কেউ কোন দিকে নেই।
ছোটবৌঠাকরুন সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে সুর নিচু করে বললেন–আপনি আর বাড়ির মধ্যে আসেন না কেন আজকাল? আমার ওপর রাগ এখনও যায়নি?
আমি অতি কষ্টে বললাম–রাগ করব কেন?
—তবে সেদিন ও-ঘরে এলেন, আমার সঙ্গে কথা বললেন না তো! চলে গেলেন কেন?
মরীয়া হয়ে বললাম–আপনাকে সেদিন চিঠি দেবো বলে এসেছিলাম, কিন্তু পাছে কিছু মনে করেন, সেজন্যে দেওয়া হয়নি। পাছে কিছু মনে করেন ভেবেই বাড়ির মধ্যে আসিনে।
তিনি খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। তার পর মৃদুস্বরে বললেন–মাথা ঠাণ্ডা করে লেখাপড়া করুন। কেন ও-রকম করেন? আর বাড়ির মধ্যে আসেন না কেন? ওতে আমার মনে ভারি কষ্ট হয়। যেমন আসতেন তেমনি আসবেন বলুন? আমায় ভাবনার মধ্যে ফেলবেন না ও রকম।
আমার শরীরে যেন নতুন ধরনের অনুভূতির বিদুৎ খেলে গেল। সেখানে আর দাঁড়াতে পারলাম না–মুখে যা এল, একটা জবাব দিয়ে নীচে নেমে এলাম। সারারাত আর ঘুমুতে পারিনে। আমার জন্যে একজন ভাবে এ চিন্তার বাস্তবতা আমার জীবনে একেবারে নতুন। নতুন নেশার মত এ অনুভূতি আমার সারা দেহমন অভিভূত করে তুললে।
কি অপূর্ব ধরনের আনন্দ-বেদনায় মাখানো দিন, সপ্তাহ, পক্ষ, মাস! দিনরাতে সব সময়ই আমার ওই ওক চিন্তা। নির্জনে কাটাই, কিছু ভাল লাগে না, অথচ যাঁর চিন্তা শয়নে-স্বপনে সর্বদাই করি, পাছে তাঁর সামনে পড়ি এই ভয়ে সতর্ক হয়ে চলাফেরা করি। লেখাপড়া, খাওয়া, ঘুম সব গেল।
বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি ছোটবৌঠাকরুনের হ’ল অসুখ। অসুখ ক্রমে বাড়াবাড়ি ধরনের হ’ল। ছাতরা থেকে যদু ডাক্তার দেখতে এল। তাঁর বাপের বাড়ি থেকে লোকজন এসে পড়ল–বাড়িসুদ্ধ লোকের মুখে উদ্বেগের চিহ্ন। আমি ডাক্তার ডাকা, ওষুধ আনা এ সব করি বাড়ির ছেলেদের সঙ্গে, কিন্তু একদিনও রোগীর ঘরে যেতে পারলাম না– কিছুতেই না। একদিন ঘরের দোরের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম–কিন্তু চৌকাঠের ওপারে যাইনি।
ক্রমে তিনি সেরে উঠলেন। একদিন আমার চয়নিকা-খানা তিনি চেয়ে পাঠালেন– দিন-দুই পরে কালো বই ফিরিয়ে দিয়ে গেল। চার-পাঁচ দিন পরে চয়নিকা-খানা কি জন্যে খুলতে গিয়েছি, তার মধ্যে একখানা চিঠি, ছোটবৌঠাকরুনের হাতে লেখা।
নাম নেই কারুর। লেখা আছে…
আমার অসুখের সময় সবাই এল, আপনি এলেন না কেন? আমি কত আশা করেছিলাম যে আপনি আসবেন, জানেন তো? আমার মরে যাওয়াই ভাল। কেন যে আবার সেরে উঠলাম! অসুখ থেকে উঠে মন ও শরীর ভেঙে গেছে। কালোর মুখে শুনেচি, আপনি ঘরে টাঙিয়ে রেখেছেন যীশুখৃস্টের ছবি, তিনি হিন্দুর দেবতা নন–কিন্তু আপনি যাকে ভক্তি করেন–আমি তাঁকে অবহেলা করতে পারিনে। আমার জন্যে তাঁর কাছে প্রার্থনা করবেন। আর-একটা কথা–একটিবার দেখতে কি আসবেন না?
যীশুখৃস্টের ছবির দিকে চাইলাম। সম্প্রতি একখানা বুদ্ধের ছবি, আর একখানা চৈতন্যের ছবিও এনে টাঙিয়েছিলাম, রোগশীর্ণা পত্রলেখিকার করুণ আকূতি ওদের চরণে পৌঁছে দেবার ভার আমার ওপর পড়েছে। কিন্তু আমি কি পারব? অনুকম্পায় মমতায় আমার মন তখন ভরে উঠেচে। যে প্রার্থনা ওদের কাছে জানালাম, তা ভাষাহীন, বাক্যহীন। আমি এ-ছাড়া আর কিছু করতে পারিনে। সামনে হঠাৎ যেতে পারব না তাঁর। এ বাড়িতেও আর বেশিদিন থাকা হবে না আমার। চলে যাব এখান থেকে।
টেস্ট পরীক্ষা দিয়েই আটঘরায় পালাবো, ঠিক করলাম। সেখানে যাইনি অনেক দিন। মা চিঠি লিখেছেন, দেখবার জন্য ব্যস্ত হয়েছেন। আমার সেখানে যেতে ইচ্ছে হয় না শুধু জ্যাঠাইমাদের ব্যবহারের জন্য। গেলেই মায়ের দুঃখ দেখতে হবে। দাদা এক বাতাসার কারখানায় চাকরি পেয়েচে, মাসে কিছু টাকা অতিকষ্টে পাঠায়। সীতা বড় হয়ে উঠল– তারই বা কি করা যায়? দাদা একাই বা কি করবে!
পিকারিং সাহেব আমার হাতে গীতা দেখে একদিন বললেন–তুমি এ-সব পড় নাকি? বাইবেল কি তোমার সকল আধ্যাত্মিক অভাব পূর্ণ করে না?
আমি বললাম–পড়ে দেখতে কি দোষ আছে সাহেব? তা ছাড়া আমি তো খৃস্টান নই, আমি এখনও হিন্দু।
–দু-নৌকাতে পা দেওয়া যায় না, মাই বয়। তুমি খৃস্টান ধর্মে দীক্ষিত হও–নয়তো তুমি বাইবেল পড় কেন?
–সাহেব, যদি বলি ইংরেজী ভাষা ভাল করে শেখবার জন্যে?
পিকারিং সাহেব হো হো করে হেসে উঠল। বললে–তোমার আত্মার পরিত্রাণ তার চেয়েও বেশি দরকারী। যীশুতে বিশ্বাস না করলে আত্মার ত্রাণ নেই। তিনি আমাদের সকলের পাপের ভার নিজে নিয়ে ক্রুশের নিষ্ঠুর মৃত্যু বরণ করেছিলেন। যীশুর ধর্মে দীক্ষিত হও, তোমার পাপ তাঁর রক্তে ধুয়ে যাবে। এস, আমার সঙ্গে গান কর।
তার পর সাহেব নিজেই গান ধরল—
Nothing but the Blood of Jesus
Oh, precious is the flow.
That can make me white as snow,
No other fount I know
Nothing but the Blood of Jesus.
পিকারিং সাহেবকে আমার খুব ভাল লাগে। খুব সরল, ধর্মপ্রাণ লোক। স্ত্রী মারা গিয়েচে আজ দশ-বারো বছর, আর বিয়ে করেননি,–টেবিলের ওপর নিকেলের ফ্রেমে বাধানো স্ত্রীর ফটো সর্বদা থাকে। মাঝে মাঝে আমায় জিজ্ঞেস করে–আমার স্ত্রী দেখতে কেমন ছিল, ভাল না? ফটো দেখে মিসেস পিকারিংকে সুন্দরী মনে হয়নি আমার, তবু বলি খুব চমৎকার।
পিকারিং সাহেবের ধর্মমত আমার কাছে কিন্তু অনুদার ঠেকে–কিছুদিন এদের সঙ্গে থেকে আমার মনে হয় জ্যাঠাইমারা যেমন গোঁড়া হিন্দু–খৃস্টানদের মধ্যেও তেমন গোঁড়া খৃস্টান আছে। এরা নিজের ধর্মটি ছাড়া আর কারুর ধর্ম ভাল দেখে না। এদের সমাজে সংকীর্ণতা আছে–এদেরও আচার আছে–বিশেষত একটা নির্দিষ্ট ধরনের ঈশ্বরের উপাসনা করলে উপাসনা ব্যর্থ হ’ল এদের মতে। একখানা কি বইয়ে একবার অনন্ত নরকের গল্প পড়লাম। শেষবিচারের দিন পর্যন্ত পাপীরা সেই অনন্ত নরকের অনন্ত আগুনের মধ্যে জ্বলবে পুড়বে, খৃস্টধর্মে দীক্ষিত হবার আগেই যদি কোন শিশু মারা যায়–তাদের আত্মাও যাবে অনন্ত নরকে। এসব কথা প্রথম যেদিন শুনেছিলাম, আমাকে ভয়ানক ভাবিয়ে তুলেছিল। তারপর মনে হল, কেন যীশু কি এতই নিষ্ঠুর? তিনি পরিত্রাণের দেবতা, তিনি সকল পাপীকেই কেন পরিত্রাণ করবেন না? যে তাঁকে জানে, যে তাঁকে না-জানে–সবাইকে সমান চোখে তিনি কেন না দেখবেন? তাঁর কাছে খৃস্টান ও অখৃস্টানে প্রভেদ থাকবে কেন? বরং যে অজ্ঞানান্ধ তার প্রতি তার অনুকম্পা বেশী হবে– আমার মনের সঙ্গে এই খৃস্টের ছবি খাপ খায়। তিনি প্রেমময় মুক্ত মহাপুরুষ, তাঁর কাছেও ধর্মের দলাদলি থাকে কখনো? যে দেশের, যে ধর্মের, যে জাতিরই হোক তিনি সবারই– যে তাঁকে জানে, তিনি তার, যে না জানে, তিনি তারও।
একদিন গঙ্গার ধারে বেঞ্চির ওপরে বসে জনকতক লোক গল্প করচে–শুনলাম বরানগরে কুঠির ঘাটের কাছে একটা বাগানবাড়িতে একজন বড় সাধু এসেচেন, সবাই দেখতে যাচ্চে। দু-এক দিনের মধ্যে একটা ছুটি পড়ল, বেলুড়ে নেমে গঙ্গা পার হয়ে কুঠিরঘাটের বাগান-বাড়ি খোঁজ করে বার করলাম। বাগানবাড়িতে লোকে লোকারণ্য, সকলেই সাধুজীর শিষ্য, মেয়েরাও আছে। ফটকের কাছে একজন দাড়িওয়ালা লোক দাঁড়িয়েছিল, আমি ফটকের কাছে গিয়ে আমার আসার উদ্দেশ্য বলতেই লোকটা দু-হাতে আমরা গলা জড়িয়ে ধরে বললে–ভাই, এস এস, তোমাকে নেওয়ার জন্যেই যে আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি।
আমি পছন্দ করিনে যে কেউ আমার গলা জড়িয়ে ধরে–আমি ভদ্রভাবে গলা ছাড়িয়ে নিলাম। লোকটা আমায় বাগানের মধ্যে নিয়ে গেল। আমি কৌতূহল ও আগ্রহের সঙ্গে চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিলাম। বাঁ-দিকের রোয়াকে একদল মেয়ে ব’সে একরাশ তরকারি কুটছে–একটা বড় গামলায় প্রায় দশ সের ময়দা মাখা হচ্ছে,–যেদিকে চাই, খাওয়ার আয়োজন।
–সাধুর দেখা পাবো এখন?
–তিনি এখন ধ্যান করচেন। তাঁর প্রধান শিষ্য জ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী ও-ঘরে আছেন, চল ভাই তোমায় নিয়ে যাই।
কথা বলচি এমন সময় একজন ভদ্রলোক এলেন, সঙ্গে একটি মহিলা–ফটকের কাছে তাঁরা মোটর থেকে নামলেন। একজন বালক-শিষ্যকে ভদ্রলোকটি কি জিজ্ঞেস করলেন– সে তাঁদের সঙ্গে করে নিয়ে এল আমার সঙ্গের দাড়িওয়ালা লোকটির কাছে। ভদ্রলোকটি তাকে বললেন–স্বামীজির সঙ্গে দেখা করতে এসেছি, তিনি কোথায়?
–কোথা থেকে আসছেন আপনারা?
—ভবানীপুর, এলগিন রোড থেকে। আমার নাম বিনয়ভূষণ মল্লিক।
দাড়িওয়ালা লোকটির শরীরের ইস্ক্রুপ কব্জা যেন সব ঢিলে হয়ে গেল হঠাৎ–সে তিন ভাগে ভেঙে হাত কচলে বললে–আজ্ঞে আসুন, আসুন, বুঝতে পেরেচি, আসুন। এই সিঁড়ি দিয়ে আসুন–আসুন মা-লক্ষ্মী।
আমি বিস্মিত হলাম। এই যে বললে সাধুজী ধ্যানে বসেচেন–তবে ওঁরা গেলেন যে! লোকটি ওঁদের ওপরে দিয়ে আবার নেমে এল। আমায় একটা হলঘরে নিয়ে গেল। সেখানে জ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারীর সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিলে। জ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারীর পরনে গেরুয়া আলখাল্লা, রং ফর্সা–আমার সঙ্গে বেশ ভালো ব্যবহার করলেন। তিনি আপিসের কাজে দেড়শো টাকা মাইনে পেতেন–ছেড়ে স্বামীজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। স্বামীজী বলেছেন তিনি তিনটে মহাদেশ উদ্ধার করবেন, সাধনায় সিদ্ধিলাভ করলেই বেরিয়ে পড়বেন সে উদ্দেশ্যে। স্বামীজীর দেওয়া মন্ত্র জপ ক’রে তিনি অদ্ভুত ফল পেয়েছেন নিজে–এই সব গল্প সমবেত দর্শকের কাছে করছিলেন। আমি কৌতূহলের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলাম–কি ফল পেয়েছেন মন্ত্রের? তিনি বললেন–মন্ত্র জপ করতে করতে মনে হয় যেন কোথায় পাহাড়ের উপরে বসে আছি। স্বামীজি বলেন–এ একটা উচ্চ অবস্থা। আমি আরও আগ্রহের সুরে বললাম–আর কিছু দেখেন? তিনি বললেন, জ্যোতিঃদর্শন হয় মাঝে মাঝে।
–সে কি রকম?
—দুই ভুরুর মাঝখানে একটা আগুনের শিখার মত দীপ্তি দেখতে পাই।
আমি হতাশ হলাম। আমি নিজে তো কত কি দেখি! এরা তো সে-সব কিছু দেখে বলে মনে হয় না। এরা আর কতটুকু দেখেচে তা হলে? পাহাড়ের ওপর বসে আছি এই দেখলেই বা কি হ’ল? ভুরুর মধ্যে আগুনের শিখা দেখলেই বা কি?
শুনলাম বেলা ছ’টার পরে স্বামীজীর দেখা পাওয়া যাবে। পাশের একটা ঘরে বসে রইলাম খানিকক্ষণ। আরও একজন বৃদ্ধ সেখানে ছিলেন। কথায় কথায় তিনি বললেন– দেখ তো বাবা–এই তোমরাও তো ছেলে। আর আমার হতচ্ছাড়া ছেলেটা পালিয়ে এসে বাড়ি থেকে এই সন্নিসির দলে যোগ দিয়েছে। এখানে তো এই খাওয়া এই থাকা। যাত্রার দলের মত এক ঘরে একশো লোক শোয়। ছেলেটার হাড়ির হাল হয়েচে–আগে একবার ফিরিয়ে নিতে এসেছিলাম–তা যায়নি। এবার আমি আসছি শুনে কোথায় পালিয়েচে হতভাগা। আহা কোথায় খাচ্ছে কি হচ্চে–এদিকে বাড়িতে ওর মা অন্নজল ছেড়েছে। এই সন্নিসির দলই তাকে সরিয়ে রেখেচে কোথায়। আজ তিন দিন এখানে বসে আছি, তা ছোঁড়া এল না। এরা তলায় তলায় তাকে খবর দিচ্ছে। আবার আমার ওপর এদের রাগ কি? বলচে ছেলে তোমার মুক্তির পথে গিয়েছে, বিষয়ের কীট হয়ে আছ তুমি, আবার ছেলেটাকে কেন তার মধ্যে ঢোকাবে? শোন কথা। ওদের এখানে বিনি পয়সার চাকর হাতছাড়া হয়ে যায় তা হ’লে যে! আমায় এই মারে তো এই মারে। দু-বেলা অপমান করছে।
–কোথা থেকে আপনার ছেলে এদের দলে এল?
–এই সন্নিসির দল গেছল আমাদের মাদারিপুরে। খুব কীর্তন করে ভিক্ষে ক’রে শিষ্য-সেবক তৈরি করে বেড়াল ক’দিন। সেখান থেকে ছেলেটাকে ফুসলে নিয়ে এসেচে।
পয়সা হাতে থাকত আমার তো ব্যাটার খাতির করত। এখানে খেতে দেয় না ওই বাজারের হোটেল থেকে খেয়ে আসি। একটু এই দালানটাতে রাত্রে শুয়ে থাকি, তাও দু বেলা বলচে- বেরো এখান থেকে। ছোঁড়াটা ফিরে আসবে, সেই আশায় আছি।
স্বামীজীর সঙ্গে দেখা হ’ল না। দেখার ইচ্ছেও আর ছিল না।
সন্ধ্যার পরে স্টীমারে পার হয়ে বেলুড়ে এলাম মনে কত আসা নিয়ে গিয়েছিলাম ওবেলা। মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবহার যেখানে ভাল নয়, সেই জ্যাঠাইমাদের বাড়ির গোপীনাথ জিউ-এর পুজোর সময় যা দেখেচি, হীরুঠাকুরের প্রতি তাদের ব্যবহার যা দেখেচি–সেই সব একই যেন।
দিন দুই পরে ছোটবৌঠাকরুনের বাপের বাড়ি থেকে বড় ভাই তাকে নিতে এল। আমার সঙ্গে দশ-পনেরো দিন দেখা হয়নি, ভাবলুম যাবার সময় একবার দেখা করবই। দুপুরের পরে ঘোড়ার গাড়িতে জিনিসপত্র ওঠানো হচ্ছে, আমি নিজের ঘরের জানলা দিয়ে দেখছি আর ভাবচি ওঠবার সময় গাড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়াব, না ওপরে গিয়ে দেখা করে আসব?
পায়ের শব্দে পেছনে চেয়ে দেখি ছোটবৌঠাকরুন দোরের কাছে দাঁড়িয়ে রোগশীর্ণ মুখে, হাতায় লাল পাড় বসানো ব্লাউজ গায়ে, পরনে লালপাড় শাড়ী। আমি থতমত খেয়ে বললাম–আপনি! আসুন, এই টুলটাতে–
তিনি মৃদু, সহজ সুরে বললেন–খুব তো এলেন দেখা করতে!
—আমি এখুনি যাচ্ছিলাম, আপনি এলেন, তাই নইলে
— ছোটবৌঠাকরুন ম্লান হেসে বললেন–না, নিজেই এলাম। আর আপনার সঙ্গে কি দেখা হবে? আপনি তো পরীক্ষা দিয়ে চলে যাবেন। বি.এ. পড়বেন না?
আমি একটু ইতস্তত করে বললাম–ঠিক নেই, এখানে হয়ত আর আসব না।
তিনি বললেন–কেন আর এখানে আসবেন না?
আমি কোন কথা বললাম না। দুজনেই খানিকক্ষণ চুপচাপ।
তারপর তিনি আমার কাছে এগিয়ে এসে মৃদু অনুযোগের সুরে বললেন–আপনার মত ছেলে যদি কখনও দেখেচি! আগে যদি জানতাম তবে সেবার আপনাকে নিয়ে যে ওরা ঠাট্টা করেছিল, আমি তার মধ্যে যাই? এখন সে-কথা মনে হলে লজ্জায় ইচ্ছে হয় গলায় বঁটি দিয়ে মরি।
তারপর গভীর স্নেহের সুরে বললেন-না, ও-সব পাগলামি করে না, আসবেন এখানে, কেন আসবেন না, ছিঃ–
দরজার কাছে গিয়ে বললেন–না এলে বুঝবো আমায় খুব ঘেন্না করেন, তাই এলেন না।
.
০৭.
দাদা কালীগঞ্জে একটা বাতাসার কারখানায় কাজ করে। অনেকদিন তার সঙ্গে দেখা হয়নি, কিছু টাকার দরকারও ছিল, কারণ কলেজের কিছু বাকী মাইনে ও পরীক্ষার ফি এর টাকার অভাব হওয়াতে শৈলদি লুকিয়ে ষোলটা টাকা দিয়েছিল। যাওয়ার আগে সে টাকা তাকে দিয়ে যাওয়া দরকার, যদিও সে চায়নি। বাঁশবেড়ের ঘাটে গঙ্গা পার হয়ে ওপারে যাব, খেয়ার নৌকো আসতে দেরি হচ্ছে, আমি প্রকাণ্ড একটা পুরোনো বাঁধাঘাটের সিঁড়িতে বসে অপেক্ষা করছি। ঘাটের ওপরে একটা জীর্ণ প্রাচীন শিবমন্দির, তার ফাটলে ফাটলে বট-অশ্বত্থের গাছ, মন্দিরের চূড়ার ত্রিশূলটা পশ্চিমে হেলে-পড়া সন্ধ্যার সূর্যের। আলোয় মনে হচ্চে যেন সোনার। ভারি ভাল লাগছিল মন্দিরটা, আর এই জনবিরল বাঁধাঘাট। ওই মন্দিরে যদি আরতি হ’ত এই সন্ধ্যায়, বন্দনারত নরনারীর দল ওই ভাঙা চাতালে দাঁড়িয়ে রইত তবে আমার আরও ভাল লাগত। কথাটা ভাবছি, এমন সময় আমার শরীরটা যেন কেমন করে উঠল, কানের পাশটা শিরশির করতে লাগলো। হঠাৎ আমার মনে হ’ল এই ঘাটের এই মন্দিরে খুব বড় একজন সাধুপুরুষ আছেন, তাঁর দীর্ঘ চেহারা, মাথায় বড় বড় চুল, প্রসন্ন হাসিমাখানো মুখ। আমি তাঁকে দেখতে পেলাম না। কিন্তু তাঁর উপস্থিতি অনুভব করলাম। তিনি এখানে অনেকদিন আছেন, ভাঙা ঘাটের রানায় বসে ওপারের উদীয়মান পূর্ণচন্দ্রের দিকে চেয়ে এই সন্ধ্যায় তিনি উপাসনা করেন–এবং তিনি কারও ওপর রাগেন না। কত লোক না বুঝে ঘাটের নির্জনতা ভঙ্গ করে, তিনি সদাই প্রসন্ন, সকলের ওপরে সদাই স্নেহশীল।
এ-রকম যখন হয়, তখন আমার শরীর যেন আমার নিজের থাকে না–নয়ত আমার সাধারণ অবস্থা থাকলে জিজ্ঞেস করতুম অনেক কথাই তাঁকে। একটু পরে খেয়া নৌকো এল–অনিচ্ছার সঙ্গে ঘাট ছেড়ে নৌকোতে উঠলাম। জায়গাটা পবিত্র প্রভাবে ভরা–এমন একটা প্রভাব, যা সে-দিন বরানগরের বাগানবাড়ির সেই সাধুর কাছে গিয়ে অনুভব করিনি।
দাদা আমায় দেখে খুব খুশী হ’ল। ওর চেহারা বড় খারাপ হয়ে গিয়েছে, ছেলেবেলাকার দুধে-আলতা রঙের সেই সুশ্রী বালককে দাদার মধ্যে আর চিনে নেওয়া যায় না। একে লেখাপড়া শিখলে না, তার ওপরে এই সব পাড়াগাঁয়ে চাকরি করে বেড়ায়–চেহারায়, বেশভূষায়, কথাবার্তায় দাদা হয়ে গিয়েচে যেন কেমন। তেমনি ধরনের লোকের সমাজে সর্বদা চলে ফেরে।
রাত তখন প্রায় ৯টা, দাদা ফিরে এসে রান্না চড়ালে। কি বিশ্রী জায়গাতেই থাকে। বাতাসার কারখানাটা একটা প্রকাণ্ড লম্বা চালাঘর–ছ-সাতটা বড় বড় উনুনে দিনরাত গনগনে আগুন–বড় বড় কড়ায় গুড়ের রস আর চিনির রস তৈরি হচ্ছে। এই কারখানায় অত আগুনের তাতে থাকা কি দাদার অভ্যেস আছে কোনকালে!
দাদা নিজেই রান্না চড়ালে। আমায় বললে–খিচুড়ি খাবি জিতু? বেশ ভাল মুগের ডাল আছে–ভাঁড়ে দেখি ঘি আছে বোধ হয় একটু–
দাদার বাসা ছোট একখানা চালাঘর। মেঝের ওপর শোয়, বিছানা পাতাই থাকে, কোনকালে তোলা হয় না, তবে খুব ময়লা নয়–আমরা ক’ ভাইবোন ময়লা জিনিসপত্র মোটেই ব্যবহার করতে পারি নে, ছেলেবেলা থেকেই অভ্যেস। বিছানার ওপরকার কুলুঙ্গিতে খবরের কাগজ পাতা, একখানা ভাঙা পারা বার-হওয়া আর্শি, আর একখানা শিঙের চিরুনি।
দাদা ছিল আমাদের মধ্যে সব চেয়ে ছেলেমানুষ, সব চেয়ে আনাড়ি, তাকে এখন নিজে রান্না করে খেতে হচ্ছে! অথচ কি-ই বা জানে ও সংসারের, কি কাজই বা পারে?
রান্না চড়িয়ে দাদা বললে–ভাল কথা, দাঁড়া জিতু, তোর জন্যে একখানা ইংরিজি বই রেখে দিইচি–বের করে দিই–
টিনের ছোট তোরঙ্গ খুলে একখানা মোটা ইংরিজি বই আমার হাতে দিয়ে বললে– এখানে সাতুবাবু কন্টাকটর আসে বাতাসা নিতে, সে ফেলে গিয়েছিল আর ফিরে আসেনি। আমি তুলে রেখে দিইচি, ভাবলাম জিতু পড়বে–
পাতা উল্টে দেখি একটা বিলিতি স্টীল কোম্পানীর মূল্যতালিকা–খুব চমৎকার পাতা, চমৎকার ছাপা, বাড়িঘর, রেলের পুল, কড়িরগার ছবিতে ভর্তি। দাদার ওপরে দুঃখ হ’ল বেচারি এ সব পড়তে পারে না, বুঝতেও পারে না–ভেবেচে কি অপূর্ব বই-ই না জানি।
আমি কিছু না বলে বইখানা আমার পুঁটুলিতে বেঁধে নিলাম। দাদা ততক্ষণে তোরঙ্গ হাতড়ে আর একখানা ছোট ছেলেদের গল্পের বই বার করে বললে–আর এই দ্যাখ একখানা বই, ভারি মজার মজার গল্প–আমি খেয়েদেয়ে রোজ একটুখানি করে পড়ি—‘খোঁড়া শিকারী’র গল্পটা পড়ছিলাম, পড় দেখি শুনি?
এ-সব গল্প ইংরিজিতে কতবার পড়েছি, আমার কাছে এর নতুনত্ব নেই কোথাও। তবুও দাদাকে পড়ে পড়ে শোনাতে লাগলাম, দাদা মাঝে মাঝে খিচুড়িতে কাঠি দিয়ে দেখে, আর হাঁটু দুটো দু-হাতে জড়িয়ে একটুখানি পেছনে হেলান দিয়ে ব’সে আমার মুখের দিকে আগ্রহের সঙ্গে চেয়ে চেয়ে শোনে। আমার এমন কষ্ট হল! এ-সব গল্প যে ইংরিজি স্কুলের নীচের ক্লাসের ছেলেরাও জানে। আহা, দাদা বড় অভাগা, অল্প বয়সে সংসারের চাপ ঘাড়ে পড়ে সারাজীবনটা ওর নষ্ট হয়ে গেল।
টাকার কথাটা দাদাকে বলতে মন চাইল না। ওর কত কষ্টে রোজগার করা পয়সা একটা আধটা নয়, ষোলটা টাকা–এগারো টাকা মাসে মাইনে পায়–ওর দেড় মাসের রোজগার কোথা থেকে দেবে ও? শৈলদির টাকা আমি এর পরে যে ক’রে হয় শোধ করে দেবো।
দাদা নিজেই বললে–বাড়ি যাবি তো জিতু, গোটা দশেক টাকা নিয়ে যা। আমার বড় ইচ্ছে সীতাকে একছড়া হার গড়িয়ে দিই–কিন্তু টাকাই জমে না হাতে। তোর টাকার যদি দরকার থাকে, তবে আলাদা-করা হারের জন্যে কুড়িটা টাকা তোলা আছে–তাই থেকে নিয়ে যা, দেবো এখন। হার এর পর দেখব।–সাত-পাঁচ ভেবে টাকা নেওয়াই ঠিক করলাম। শৈলদির ওপর বড় জুলুম করা হয়, নইলে শৈলদিকে মনে হয় না যে সে পর। এত আপনার মত ক’জন আপনার লোকই বা দেখে? মায়ের পরেই শৈলদিকে ভক্তি করি। সে লুকিয়ে টাকা দিয়েছে–তাকে আর বিপন্ন করবো না।
যে দাদা সকাল আটটার কমে বিছানা থেকে উঠত না, তাকে ভোর পাঁচটার সময় উঠে কারখানায় গিয়ে কাজে লাগতে হয়। আমিও দাদার সঙ্গে গেলাম। কারখানার মালিকের নাম মতিলাল দাস, বয়েস পঞ্চাশের ওপর, তৃতীয়পক্ষের স্ত্রী আছে সংসারে, আর দ্বিতীয় পক্ষের ছেলেমেয়ে। দাদা মতিলালের তৃতীয়পক্ষের স্ত্রীকে মাসীমা বলে ডাকে ৷ মতিলাল আমায় দেখে বললে–তুমি নিতাই ঠাকুরের ভাই? বেশ, বেশ। আজকাল কি বই পড়ায় তোমাদের?
তার প্রশ্ন শুনে আমার হাসি পেল। আমি জবাব দেবার আগেই মতিলাল বললে– আমাদের সময়ে যে-সব বই পড়ানো হ’ত, আজকাল কি আর সে-সব বই আছে? এই ধর পদ্যপাঠ, তৃতীয় ভাগ, যদুবাবুর। আহা!
কুব্জ্যপৃষ্ঠ নুযব্জদেহ উষ্ট্র সারি সারি
কি আশ্চর্য শোভাময় যাই বলিহারি
কি সব শব্দ লাগিয়েচে দেখেচ একবার? ভাষার জ্ঞান হ’ত কত পড়লে! বলো দিকি নুযব্জদেহ মানে কি? আমাদের হরিশ পণ্ডিত পড়াত কালনার স্কুলে, আমি তখন ছাত্রবৃত্তি পড়ি। তখন ছাত্রবৃত্তি পড়লে মোক্তার হ’ত, দারোগা হ’ত। এখন হয়েচে তো সব ছেলেখেলা।
আমি এসেছি শুনে মতিলালের স্ত্রী দুপুরে খেতে বললে। আমায় দেখে বললে–এস বাবা, তুমি নিতাইয়ের ভাই? তুমিও মাসীমা বলে ডেকো। কাছে দাঁড়িয়ে থেকে মাসীমা দাদাকে রান্না দেখিয়ে দিতে লাগল, কারণ আমরা খেতে চাইলেও ওরা রেঁধে আমাদের খেতে দেবে কেন?
মাসীমা সংসারে নিতান্ত একা। মতিলালের ও-পক্ষের ছেলেমেয়েরা বাপের তৃতীয় পক্ষের পরিবারকে দু-চোখ পেড়ে দেখতে পারে না, বা এখানে থাকেও না কেউ। অথচ মাসীমার ইচ্ছে তাদের নিয়ে মিলেমিশে সংসার করা। আমরা খেতে বসলে কত দুঃখ করতে লাগল।
–এই দ্যাখো বাবা, কেষ্টকে বলি বৌমাকে নিয়ে এখানে এস, এসে দিব্যি থাক। বৌমাটি বড় চমৎকার হয়েছে। তা যদি আসে! সেই নিয়ে রেখেচে শ্বশুরবাড়ি, কালনার কাছে দাঁইহাট–সেখানেই থাকে। আমার নিজের পেটে তো হ’ল না কিছু, ওরাই আমার সব–তা এমুখো হয় না কেউ। বড় মেয়ে দুটি শ্বশুরবাড়ি আছে, আনতে পাঠালে বলে, সৎমায়ের আর অত আত্যিসূয়ো দেখাতে হবে না। শোন কথা। আমায় মা বলে কেউ ডাকেও না। ডাকলে তাদের মান যাবে।
মাসীমাকে খুশী করবার জন্যে আমি কারণে-অকারণে খুব মাসীমা মাসীমা বলে ডাকতে লাগলাম। আমাদের পাতে আবার মাসীমা খেতে বসলেন, বললেন- ব্রাহ্মণের পেরসাদ পাবো, ওতে কি আর ছোট বড় আছে বাবা?
আমার মনে অস্বস্তি হ’ল আমি তো এঁদের এসব মানিনে, ব্রাহ্মণের ধর্ম পালন করিনে, সে কথা তো ইনি জানেন না। অথচ খুলে বললে মাসীমার মনে কষ্ট দেওয়া হবে হয়ত।
দাদার কাছ থেকে আটঘরায় এলাম। আসবার সময় সীতার জন্যে ভাল সাবান কিনে নিয়ে এলাম, বই পড়তে ভালবাসে ব’লে দু-তিনখানা বাংলা বইও আনলাম। সীতা বড় হয়ে উঠেচে–মাথায় খুব লম্বা হয়েচে, দেখতে সুন্দর হয়েছে আরও।
আমার হাত থেকে সাবান নিয়ে হেসে বললে–দেখি দাদা কেমন সাবান…আমার একখানাও আস্ত সাবান ছিল না। একখানা সানলাইট সাবান আনিয়েছিলুম বাজার থেকে–সে আধখানা হয়ে গিয়েছে।
সীতার সে পুরোনো অভ্যাস এখনও আছে, কথা বলতে বলতে হঠাৎ খোঁপায় হাত দিয়ে দেখে ঠিক আছে কি-না। লম্বা ঢেঙা, চওড়া নক্সা-পাড় কাপড় পরনে, খোঁপার ধরনও আজকাল শহরে দেখে এসেচি ও-রকম খোঁপা উঠে গিয়েচে। ও-ধরনের কাপড় পরলে সেখানে লোকে হাসবে, বেচারী সীতা! লেখাপড়া শেখবার, বই পড়বার ওর কত আগ্রহ! অথচ এই পাড়াগাঁয়ে পরের বাড়ি দাসীবৃত্তি করেই ওর জীবন কাটল। না হ’ল লেখাপড়া শেখা, না মিটল কোনো সাধ। অথচ ওর বুদ্ধি ছিল এত চমৎকার, মিশনারী মেমেরা কত প্রশংসা করত, ওকে কি ভালই বাসত মিস নর্টন। কিন্তু কি হ’ল ওর? এখনও সেই কতকাল আগেকার পুরোনো বইগুলোই পড়চে, কিছুই শেখেনি, কিছুই দেখেনি।
সীতা বললে–দাদা পাস করেচ?
—পাসের খবর এখনও বেরোয়নি। পাস করবো ঠিকই।
—পাস হ’লে আমায় জানিও দাদা। আমি তোমাকে একটা জিনিস প্রাইজ দেবো!
—কি জিনিস রে?
–একটা মনিব্যাগ বুনচি লাল উলের। তোমার জন্যে একটা, বড়দার জন্যে একটা। তোমাদের নাম লিখে দেবো। মিস নর্টন আমাদের দিত কত কি প্রাইজ–না?
–মিস নর্টনকে তোর মনে আছে সীতা? তুই তো তখন খুব ছোট।
–খুব মনে আছে, তার দেওয়া জিনিস আমার বাক্সে এখনও রয়েছে। দেখলেই তাদের কথা মনে পড়ে।
জ্যাঠামশায় আমাকে ডেকে বললেন–জিতু শোনো। এখন তুমি বড় হয়েচ, তোমার সঙ্গে পরামর্শ করে কাজ করাই ভাল। সীতার বিয়ে না দিলে নয়। ওর পনের-ষোল বছর হ’ল, আর ঘরে রাখা যায় না। কিন্তু এদিকে টাকাকড়ি খরচ করবে কে? হাজার টাকার কমে আজকাল ভদ্রলাকের ঘরের বিয়ের কথাই তোলা যায় না। দেখে এসেচ তো শহর বাজারে? তা আমি এক জায়গায় ঠিক করেচি পাত্রটির বাপ আমার এখানে এসেছিল। জমিজমা আছে, চাষা গেরস্ত, খেতে পরতে কষ্ট পাবে না। আখের চাষই আছে অমন বিশ-বাইশ বিঘে। পাত্রটি চাষবাস দেখে, রং একটু কালো–তা হোক, পুরুষ মানুষের রঙে কি আসে যায়, তবে বংশ ভাল, কামদেব পণ্ডিতের সন্তান, সবে তিন পুরুষে ভঙ্গ, আমাদেরই স্বঘর।
আমি বললাম–লেখাপড়া কতদূর করেচে?
–লেখাপড়া কি আর এম-এ, বি-এ পাস করেছে? তবে বাংলা ছাত্রবৃত্তি পর্যন্ত পড়েছে, দিব্যি হাতের লেখা। হ্যাঁ, একটা কথা ভুলে যাচ্ছি,–অল্পদিন হ’ল পাত্রটির প্রথম পক্ষের স্ত্রী মারা গিয়েছে–তবে সে কিছু নয়, বয়েস কমই। একটি বুঝি ছেলে আছে ও-পক্ষের।
ছাত্রবৃত্তির কথায় আমার মতিলালের উটের কবিতাটি মনে পড়ল। আমি বললাম– আচ্ছা আমি ভেবে বলব জ্যাঠামশাই। লেখাপড়া জানে না আর তাতে দোজবরে, এতে বিয়ে দেওয়া আমার মন সরে না। সীতার মত মেয়ে, আপনি বলুন না জ্যাঠামশাই?
জ্যাঠামশাই নিজের কথার প্রতিবাদ সহ্য করতে পারেন না–তিনি এ অঞ্চলের মানী ব্যক্তি, আগের চেয়ে বিষয়-আশয় টাকাকড়ি এখন তাঁর আরও বেশী, এদিকের সব লোক তাঁকে খাতির করে চলে, কেনই বা তিনি প্রতিবাদ সহ্য করবেন? সে জানি এ গাঁয়ের রাম বাঁড়ুয্যের ব্যাপারে। রাম বাঁড়ুয্যে কি জন্যে রাত্রে আফিম খেয়ে শুয়েছিল–সকালে উঠে খবর পেয়ে জ্যাঠামশায় গেলেন। রাম বাঁড়ুয্যে ছিল জ্যাঠামশায়ের খাতক। জ্যাঠামশায় গিয়ে কড়া সুরে বললেন–কি হয়েছে রাম? রাম বাঁড়ুয্যে তখন কথা বলতে পারছে না– জ্যাঠামশায়ের কথার উত্তর সে দিতে পারল না। জ্যাঠামশায় ভাবলেন, বাঁড়ুয্যে তাঁর প্রতি অসম্মান দেখিয়ে ইচ্ছে করেই কথার উত্তর দিচ্ছে না। বললেন–ভাল ক’রে কথার উত্তর দাও–কার সামনে কথা বলচ জান না? সঙ্গের সব লোক বললে–হাঁ, কর্তা যা বলচেন, জবাব দাও ওঁর কথার। কিন্তু রাম বাঁড়ুয্যে জ্যাঠামশায়ের চোখরাঙানির চোহদ্দি পার হয়ে চলে গেল ঘণ্টা দুইয়ের মধ্যেই–কি জন্যে সে আফিম খেয়েছিল কেউ জানে না–তার মৃত্যুর পরে জ্যাঠামশায় তার ভিট্মোটি বিক্রী করে নিয়ে নিলেন–তার বিধবা স্ত্রী নাবালক একটি মাত্র মেয়ের হাত ধরে ভাইদের দোরে গিয়ে পড়লো। আমি যেবার ম্যাট্রিক দিই, সে বছরের কথা।
আমার কথার উত্তরে জ্যাঠামশায় আমায় অনেকগুলা কথা শুনিয়ে দিলেন। আমাদের এদিক নেই, ওদিক আছে। রাজামহারাজাদের ঘরে বোনের বিয়ে দেবার ইচ্ছে থাকলেই তো হয় না, পয়সা চাই। পনের-ষোল বছরের মেয়ে গ্রামে সমাজের মধ্যে বাস করতে গেলে আর ঘরে রাখা চলে না। তা ছাড়া তিনি কথা দিয়ে ফেলেচেন–তাঁর কথার মূল্য আছে ইত্যাদি।
জ্যাঠামশায়দের বাড়ির জীবনযাত্রার ধারা সেই পুরোনো দিনের মতই চলেছে। এখানে এলেই বুঝি এদের মন নানা দিক থেকে কত ভাবে শৃঙ্খলিত। বাড়িতে এতটা জমি রয়েচে, ঠাকুরপূজার উপযোগী ছোট্ট একখানা গাঁদা ও করবী ফুলের বাগান ছাড়া আর কোথাও একটা ফুলের গাছ নেই। উঠোনের কোনো জায়গায় এরা কোথাও একটু সবুজ ঘাস রাখবে না–মেজকাকার কাজ হচ্চে এতটুকু কোথাও ঘাস গজালে তখনি নিজের হাতে নিড়েন ধরে উঠিয়ে ফেলা। প্রকাণ্ড উঠোন চাঁচাছোলা, সাদা মাটি বার করা, সবুজের লেশ নেই। ব’লে দেখেচি এরা তা বোঝে না। সামনের উঠোনটা লাউ-মাচা, পুঁই-মাচায় ভরা–প্রত্যেক জায়গাটুকুতেই তরকারি লাগিয়েছে, নয়ত মান-কচুর ঝাড়।
একদিন জ্যাঠামশায়ের ছেলে হারুদাকে বললাম–আমি শ্রীরামপুর থেকে ভাল মরসুমী বীজ এনে দেবো আর এক রকম লতা আছে আমাদের কলেজে, চমৎকার নীল ফুল ফোটে। বাড়ির সামনেটা বাগান করো আর চণ্ডীমণ্ডপের চালে সেই লতা উঠিয়ে দাও–
হারুদা বললে–তোমার যেমন বুদ্ধি, ফুলগাছে কি দুধ দেবে শুনি? মিছিমিছি জায়গা জোড়া–চণ্ডীমণ্ডপের চালে ফি বছর ত্রিশ-চল্লিশখানা চালকুমড়া হয় জানিস তা?
অর্থাৎ আহারের আয়োজন হ’লেই হ’ল, আর কিছু দরকার নেই এদের।
মেজকাকার ঘরে একদিন শুয়েছিলাম, কাকীমা এখানে নেই–মেজকাকার আবার একলা ভয় করে, তাই আমাকে শুতে বলেছিলেন। সারাদিন গরমের পরে অনেক রাত্রে এক পশলা বৃষ্টি হল–কি সুন্দর ভিজেমাটির গন্ধ আসতে লাগল–মেজকাকা দেখি উঠে তাড়াতাড়ি জানলা বন্ধ করচেন।
আমি বললাম–বন্ধ করচেন কেন মেজকাকা, বেশ ভিজে হাওয়া আসচে—
মেজকাকা বললে-উঁহু, উঁহু-ঠাণ্ডা লাগবে–শেষরাতের বিষ্টির হাওয়া বড় খারাপ, কাল সর্দি ধরবে–আমার ধাতই একে সর্দির!
দুপুরে সীতার সম্বন্ধে মাকে বললাম। মায়ের ইচ্ছে নয় ওখানে সীতার বিয়ে দেওয়া, তবে মা নিরুপায়, এ বাড়িতে তাঁর কোনো কথা খাটে না। আমি বললাম–আমি কোথাও চাকরি খুঁজে নিই মা। সীতার বিয়ে নিজে থেকে দেব।
মা বললেন–শোন কথা ছেলের। তুই লেখা-পড়া ছেড়ে এখন করবি কি? তোদের মুখের দিকে চেয়ে এখানে কষ্ট করে পড়ে থাকি। নিতুর তো কিছু হ’ল না, তুই বি-এ’টা পাস কর। সীতার কপালে যা থাকে হবে। তুই এখন চাকরিতে কত টাকা পাবি যে সীতার বিয়ে দিবি নিজে? মাঝে পড়ে তোর পড়াটা হবে না। আর শোন, এ নিয়ে কোন কথা যেন বলিস নে কারুর সঙ্গে। তোর জ্যাঠাইমা শুনতে পেলে রক্ষে রাখবে না।
মা এত ভয় করেও চলেন ওদের! প্রথম জীবনে কোন কষ্ট পান নি, তারপর চা-বাগান থেকে এসে দুঃখের মধ্যে পড়ে গিয়ে এমন ভীতু হয়ে উঠেছেন। সদাই ওঁর ভয় থাকে জ্যাঠাইমা ওঁদের দুজনকে এ বাড়িতে জায়গা দিতে না চাইলে, আমার লেখাপড়া নাহয়, সীতার বিয়ে নিয়ে দাদা জড়িয়ে পড়ে–এই সব।
সীতাকে জলে ফেলে দিতে পারব না, মা যাই বলুন।
জ্যাঠামশায়দের বাড়িতে বেশীক্ষণ থাকলে আমার হাঁপ লাগে। গাঁয়ের বাইরে নির্জন মাঠে গিয়ে বসে ভাবি সীতার সম্বন্ধে কি করা যায়। কিন্তু হঠাৎ কেমন করে অন্য চিন্তা এসে পড়ে। এই রৌদ্রালোকিত দুপুরে একা বসলেই তাঁর কথা আমার মনে পড়ে। মন থেকে দূর করতে পারি নে। প্যালেস্টাইনের ঊষর, পর্বতময় মরুদেশের রৌদ্র–সারা গায়ে ঘাম ঝরচে তাঁর, রোদে মুখ রাঙা, নিজের ভারী ক্রশটা নিজেই বয়ে চলেছেন বধ্যভূমিতে। পিছনের অন্ধ জনতা জানে না যে ঝড়ে গ্যালিলির সমুদ্রের নোনা জলে দুকূল ছাপিয়ে মাঝে মাঝে যে তরঙ্গ ওঠায়, তাও তুচ্ছ হয়ে যাবে সে বৃহত্তর তুফানের কাছে, আজকার দিনটি জগতে যে তুফান তুলবে। তারা জানে না যে মানুষের মনে ব্যথা না দেওয়ার চেয়ে বড় আচার নেই, প্রেমের চেয়ে বড় ধর্ম নেই। তাঁর আবির্ভাব কে ব্যর্থ করবে?–ঐ বজ্র-বিদুযতের মত শক্তিমান তাঁর বাণী। বিষ্ণুর সুদর্শন যে শক্তির প্রতীক। নিত্যকালের দেবতা তাঁরা, দেশের অতীত, কালের অতীত, সকল দেশের, সকল অবতারের স্বগোত্র।
তারপর আমি যেন কোথায় চলে গিয়েছি। সেখানে নদী, মাঠ, বন সবই আছে, কিন্তু সবই যেন ঝাড়লণ্ঠনের কাঁচের পরকলার মধ্যে দিয়ে দেখচি। রাত কি দিন বুঝতে পারলাম না, মাথার ওপরকার আকাশে তারা নেই। অথচ সূর্যও দেখলাম না আকাশে। আমি যেন সেখানে বেশ সহজ অবস্থাতেই আছি। একটু পরেই মনে হ’ল সে জায়গাটাতে আমি অনেক বার গিয়েচি, নতুন নয়, ছেলেবেলা থেকে কতবার গিয়েছি। একটা বাড়ি আছে সেখানে, বাড়িতে যারা আছে তারা আমার সঙ্গে গল্প করে, কত কথা বলে–স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে যেন মনে হয় তারা আমার খুব পরিচিত। কতবার তাদের দেখেচি। সেখানে গেলেই আমার মনে পড়ে যায় সেখানকার পথ-ঘাট, ওইখানে মাঠের মধ্যে একটা পুরোনো বাড়ি আছে, ওর ওপাশে সেই বনটা। সেখানে যেমনি যাই, মজা এই যে অমনি মনে হয় এ তো নতুন নয়, সেই যে একবার ছেলেবেলায় চা-বাগানে থাকতে এসেছিলাম! কিন্তু সে দেশটা যেন অন্য রকম, যখন সেখানে থাকি তখন স্বাভাবিক মনে হলেও, পরে মনে হয় সেটা এই পৃথিবীর মত নয়।
সেখানে আমি কতক্ষণ ছিলাম জানি না–উঠে দেখি গাছে ঠেস দিয়ে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, কিন্তু এত ঘুম ঘুমিয়েচি–উঠে চোখ মুছে চারিদিকে চেয়ে দেখি প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেচে। কেবল এইটুকু আমার মনে ছিল স্বপ্নের দেশে কাকে যেন জিজ্ঞেস করেছিলুম–বটগাছের নীচে একটা সুন্দর ঠাকুর আছেন, শুনেচি বিষ্ণুমূর্তি, আমার বড় ভাল লাগে–জ্যাঠাইমারা পুজো করে না কেন? ঘুম কি সত্যি, কিছুই বুঝতে পারলাম না। মনের সে আনন্দটা কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে ছিল।
জ্যাঠামশাইরা কি একটা মোকদ্দমার সাক্ষীসাবুদ দু-তিন দিন ধরে চণ্ডীমণ্ডপে তালিম দিয়ে শেখালেন। যে কেউ শুনলে বুঝতে পারতো যে এরা সে-সব জায়গায় যায়নি, কস্মিনকালেও-সে-সব ঘটনা দেখেও নি–এঁদের খামার-সংক্রান্ত কি একটা দখলের মামলা।
একদিন শুনলাম মামলায় এঁরা জিতেচেন–আবার সেই ব্যাপার দেখলুম বাড়িতে। গৃহদেবতার প্রতি ভক্তিতে আপ্লুত হয়ে উঠলেন সবাই–মহাসমারোহে পূজা হ’ল, স্বপক্ষের যারা সাক্ষী ছিল, তাদের পরম যত্নে তোয়াজ করে খাওয়ালেন। খাওয়ান তাতে ক্ষতি নেই–কিন্তু দেবতাকে এর মধ্যে জড়ান কেন?
এঁরা ভাবেন কি যে দেবতা তাঁদেরই বাঁধা, হাতধরা–ওঁদের মিথ্যাকে অবিচারকেও সমর্থন করবেন তিনি ভোগ নৈবিদ্যের লোভে?
জ্যাঠাইমা যখন ব্যস্ত হয়ে গরদের শাড়ি পরে পূজার আয়োজনে ছুটোছুটি করছিলেন, তখন আমার ভারি রাগ হ’ল–আজকাল এসব মূঢ়তা আমার আদৌ সহ্য হয় না, ছেলেবেলার মত ভয়ও করি না আর জ্যাঠাইমাকে–ভাবলুম এ নিয়ে খুব তর্ক করি, দু কথা শুনিয়ে দেবো, তাতে ওঁদের উপকারই হবে–দেবতাকে নিয়ে ছেলেখেলা বন্ধ হবে– কিন্তু সীতা ও মায়ের কথা ভেবে চুপ করে রইলুম।
.
০৮.
মাস দুই হ’ল চাকুরি পেয়েছি কলকাতায়। এ চাকুরি পাওয়ার জন্যেও আমি শৈলদির কাছে কৃতজ্ঞ। শৈলদির স্বামীর এক বন্ধুর যোগাযোগে এটা ঘটেচে। যাদের বাড়ি চাকরি করি, এরা বেশ বড় লোক।
বাড়ির কর্তা নীলাম্বর রায় হাওড়া জেলার কি একটা গ্রামের জমিদার এবং সেখানকার তাঁদেরই পূর্বপুরুষের প্রতিষ্ঠিত এক মঠের বর্তমান মালিক–এদের মঠের অধীনে একটা ধর্মসম্প্রদায় গড়ে উঠেচে গত ষাট-সত্তর বছরে এবং এঁরাই সেই সম্প্রদায়ের ধর্মগুরু। বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম এই তিন জেলাতে এই সম্প্রদায়ের লোক যত বেশী, অন্য জেলাতে তত নয়। ওঁদের কাগজপত্র ও দেশের নায়েবের সঙ্গে ওঁদের যে চিঠিপত্র লেখালেখি হয়েছে–তা থেকেই আমি এ-সব সংবাদ জানতে পারলাম অল্পদিনের মধ্যেই। এঁদের প্রধান আয় বৈশাখ মাসে মঠবাড়ির মহোৎসব থেকে—-নানা অঞ্চল থেকে শিষ্যসেবকের দল জড়ো হয়ে সেই সময় বার্ষিক প্রণামী, পূজা, মানত শোধ দেয়–তা ছাড়া বিবাহ ও অন্নপ্রাশনের সময়ও মঠের গদিতে প্রত্যেক শিষ্যের কিছু প্রণামী পাঠিয়ে দেওয়া নিয়ম।
নীলাম্বরবাবুর তিন ছেলেই ঘোর শৌখিন ও উগ্র ধরনের শহুরে বাবু। বড় ছেলে অজয়বাবু এঞ্জিনিয়ারীং পড়েছিলেন কিন্তু পাস করেন নি–মেজ ছেলে নবীনবাবু এম-এ পাস, ছোট ছেলে অমরনাথ এখনও ছাত্র–প্রেসিডেন্সি কলেজে থার্ড-ইয়ারে পড়ে। অজয়বাবুর বয়স পঞ্চাশের কম নয়, কিন্তু পোশাক-পরিচ্ছদে কুড়ি বছরের ছোকরাও হার মানে তাঁর সৌখিনতার কাছে–নবীনবাবুর বয়স চল্লিশ-বিয়াল্লিশ, লম্বা, ফর্সা, সুপুরুষ– পেছনের ঘাড় একদম ক্ষুর দিয়ে সাদা বার-করা, চোখে চশমা–প্রায়ই পরনে সাহেবী পোশাক থাকে। বাঙালী পোষাক পরলে পরেন হাত-গিলে-করা মিহি আদ্দির পাঞ্জাবি ও কোঁচানো কাঁচি ধুতি, পায়ে কালো এ্যালবার্ট জুতো।
কর্তা নীলাম্বর রায়কে আমি বেশী দিন দেখিনি। তিনি তাঁর তাকিয়া বালিশ, গড়্গড়া, পিকদানী নিয়ে দোতলাতে থাকেন। কালেভদ্রে তাঁর কাছে আমার যাওয়া দরকার হয়। বড় ছেলে অজয়বাবুই কাজকর্ম দেখাশুনো করেন–তাঁর সঙ্গেই আমার পরিচয় বেশী।
অজয়বাবু লোক মন্দ নয়–কিন্তু নবীনবাবু ও অমরনাথের মুখে প্রথম দিনেই একটা উগ্র দাম্ভিকতার ছাপ লক্ষ্য করলুম। আমি এ ধরনের লোকের সংস্পর্শে জীবনে এ পর্যন্ত আসি নি–কি জানি আমার কোন ব্যবহারে এরা কি দোষ ধরে ফেলে–সেই চিন্তা আমায় সর্বদা সন্ত্রস্ত করে তুললে।
ওদের বাড়ি হরি ঘোষের স্ট্রীটে বাড়িটার পূর্ব দিকে একটা ছোট গলি–কিন্তু সেই দিকেই বাড়ির সদর। হরি ঘোষের স্ট্রীটের দিকটা রেলিং-বসানো লম্বা বারান্দা–বারান্দায় উঠবার সিঁড়ি নেই সেদিকে। রাস্তার ওপরের ছোট ঘরটাতে আমার থাকবার জায়গা নির্দিষ্ট হ’ল। এই ঘরে আমি যে একলা থাকি তা নয়, পাশাপাশি নীচু চার-পাঁচটা তক্তাপোশের ওপর ঢালা ফরাস পাতা, তার ওপর রাত্রে যে কত লোক শোয় তার হিসেব রাখা শক্ত। এদের এদেশের কাছারীর নায়েব কুঞ্জ বসু প্রায়ই আসে কলকাতায়, সে আমার পাশেই বিছানা পাতে, তার সঙ্গে একজন মুহুরী আসে, সে নায়েবের পাশে শোয়। বাড়ির দুজন চাকর শোয় ওদিকটাতে। ওস্তাদজী বলে একজন গানের মাস্টার বাড়ির ছেলেমেয়েদের গান ও হারমোনিয়াম বাজাতে শেখায়–সে আর তার একজন ভাইপো শোয় চাকরদের ও আমাদের মধ্যে। এতগুলো অপরিচিত লোকের সঙ্গে একসঙ্গে শোয়া কখনো অভ্যেস নেই–প্রথম দিনেই এদের গল্পগুজব, হাসি-কাশি, তামাকের ধোঁয়া আমাকে অতিষ্ঠ করে তুললে। সীতার মুখ মনে করে সব অসুবিধাকে সহ্য করবার জন্যে প্রস্তুত হই।
একদিন আমি সেরেস্তা-ঘরে বসে কাজ করচি–হঠাৎ দেখি মেজবাবু ঘরে ঢুকেচেন। আমি মেজবাবুকে দেখে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালাম। মেজবাবু চারদিকের দেওয়ালের দিকে চোখ তুলে বললেন–এ ঘরের এই ছবিগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্চে, তুমি নজর রাখো না?
মেজবাবুর সামনাসামনি হওয়া এই আমার প্রথম। আমাকে ‘তুমি’ বলে সম্বোধন করতে আমি মনে আঘাত পেলাম এবং আমার ভয়ও হ’ল। তা ছাড়া ছবি নষ্ট হওয়ার কৈফিয়ৎ আমি কি দেবো বুঝতে না পেরে চুপ করে আছি, এমন সময় মেজবাবু বাজখাঁই আওয়াজে ডাকলেন–দৈতারী–
দৈতারী সেরেস্তার কালির বোতল গুনে গুনে আলমারিতে তুলছিল পাশের ঘরে, সে ঘরের পাশে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে বললে–হুজুর–
–এই উল্লুক, তুমি দেখতে পাও না ঘরের ছবিগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে?
দৈতারী ঘরের দেওয়ালের দিকে বিপন্ন মুখে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।
মেজবাবু হঠাৎ আমার ডেস্ক থেকে রুলটা তুলে নিয়ে তাকে হাতে পিঠে ঘা-কতক বসিয়ে দিয়ে বললেন–স্টুপিড পাজি, বসে বসে শুধু মাইনে খাবে? এক ডজন চাকর বাড়িতে মাইনে দিয়ে রাখা হয়েছে শুধু ফাঁকি দেবার জন্য? পাড়ো ছবিগুলো এক-একখানা ক’রে–পাড়ো আমার সামনে–
দৈতারীর সে রুলের ঘা যেন আমার পিঠেই পড়ল। আমি ভয়ে ভয়ে দৈতারীকে ছবি পাড়তে সাহায্য করতে লাগলুম। আমি সামান্য মাইনের চাকুরি করি–মেজবাবু আমাকেও ঠেস দিয়ে কথাটা বললেন। তারপর আধঘণ্টা তিনি ঘরে দাঁড়িয়ে রইলেন–আমি ও দৈতারী তাঁর সামনে সমস্ত ছবিগুলো একে একে পেড়ে পরিষ্কার করলাম। সাহস করে যেন মাথা তুলে চাইতে পারলাম না, যেন আমি নিজেই ছবির তদারক না করে প্রকাণ্ড অপরাধ করে ফেলেছি।
সেইদিন প্রথম বুঝলাম আমার মত সামান্য মাইনের লোকের কি খাতির–আর কি মান এদের কাছে। সীতার বিয়ের একটা বন্দোবস্ত করতে পারি তবে আবার পড়বো। ছোট বৌঠাকরুনের কথা এই সময় মনে হ’ল–শৈলদির কথাও মনে পড়ল। কত ধরনের মানুষই আছে সংসারে! অমরনাথবাবুর বৈঠকখানা আমাদের ঘরের সামনে। খুব শৌখীন জিনিসপত্র সাজানো এবং প্রত্যেক দিনই কোন-না-কোন শৌখীন জিনিস কেনা লেগেই আছে। সে ঘরে রোজ সন্ধ্যার পর বন্ধুবান্ধবেরা এসে গানের আড্ডা বসায়–কেউ ডুগি-তবলা, কেউ হারমোনিয়াম বাজায়–গান-বাজনায় অমরবাবুর খুব ঝোঁক। সে-দিন আড়াইশো টাকার একটা গানের যন্ত্র রাখবার কাঁচের আলমারি কেনা হ’ল। তিনি কলেজের ছাত্র বটে, কিন্তু আমি পড়াশুনা করতে একদিনও দেখিনি তাঁকে। একদিন বেলা দশটার সময় অমরনাথবাবু ঘরে ঢুকে বললেন–ওহে, পাঁচটা টাকা দাও তো, আছে তোমার কাছে?
আমি প্রথমটা অবাক হয়ে গেলাম। আমার কাছে টাকা চাইতে এসেছেন ছোটবাবু! ব্যস্তভাবে আমার বাক্সটা খুলে টাকা বার করে সসম্ভ্রমে তাঁর হাতে দিলাম। দিনকতক কেটে গেল, আর একদিন তিনটে টাকা চাইলেন। মাইনের টাকা সব এখনও পাইনি– দশটা টাকা মোটে পেয়েছিলাম–তা থেকে দিয়ে দিলুম আট টাকা। দু-তিন মাসে ছোটবাবু আমার কাছে পঁচিশ টাকা নিলেন–বাড়ির ও আমার হাতখরচ বাদে যা-কিছু বাড়তি ছিল, সবই তাঁর হাতে তুলে দিলাম।
একদিন দাদা চিঠি লিখলে–তার বিশেষ দরকার। পনেরটা টাকা যেন আমি পাঠিয়ে দিই। আমার হাতে তখন মোটেই টাকা নেই। ভাবলুম, ছোটবাবুর টাকাটা তো দেওয়ার কথা এতদিনে–দিচ্ছেন না কেন! বড়মানুষের ছেলে, সামান্য টাকা খুচরো কিছু কিছু করে নেওয়া, সে ওঁর মনেই নেই বোধ হয়। লজ্জায় চাইতেও পারলাম না। অগত্যা বারোটা টাকা আগাম পাওয়ার জন্যে একটা দরখাস্ত করলুম। সে-দিন আপিসে আবার বসেছেন মেজবাবু। দরখাস্ত পড়ে আমার দিকে চেয়ে বললেন–কি হবে তোমার আগাম টাকা?
মেজবাবুকে আমার বড় ভয় হয়। বললুম–দাদা চেয়ে পাঠিয়েচেন, হাতে আমার কিছু নেই তাই।
মেজবাবু বললেন–তুমি কতদিন সেরেস্তায় কাজ করচ? চার মাস মোটে? না, এত কমদিনের লোককে এ্যাডভান্স দেওয়া স্টেটের নিয়ম নেই–তা ছাড়া তুমি তো এখনও পাকা বহাল হওনি–এখনও প্রোবেশনে আছ।
কই, চাকুরিতে ঢোকবার সময় সে-কথা তো কেউ বলেনি যে আমি প্রোবেশনে বহাল হচ্চি বা কিছু। যাই হোক, দরখাস্ত ফিরিয়ে নিয়ে এলাম। দাদাকে টাকা পাঠানো হ’লই না, এদিকে ছোটবাবুও টাকা দিলেন না, ভুলেই গিয়েচেন দেখচি সে-কথা। প্রথমে আসবার সময় ভেবেছিলাম এঁরা কোন দেবস্থানের সেবায়েত, সাধু-মোহান্ত মানুষ হবেন–ধর্মের একটা দিক এঁদের কাছে জানা যাবে–কিন্তু এঁরা ঘোর বিলাসী ও বিষয়ী, এখন তা বুঝচি। মেজবাবু এই চার মাসের মধ্যে এটর্নির বাড়ি পাঠিয়েচেন আমায় যে কতদিন, কোথায় জমি নিয়ে ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের সঙ্গে প্রকাণ্ড মোকদ্দমা চলচে-এ বাদে কুঞ্জ নায়েব তো প্রায়ই দেশ থেকে আপীলের কেস আনচেন। মেজবাবু মামলা-মোকদ্দমা নাকি খুব ভাল বোঝেন, কুঞ্জ নায়েব সেদিন বলছিল।
অপরে কি করে ধর্মানুষ্ঠান করে, তারা কি মানে, কি বিশ্বাস করে, এসব দেখে বেড়াতে আমার বড় ভাল লাগে।
একদিন হাওড়া পুলের ওপারে হেঁটে অনেক দূর বেড়াতে গেলুম। এক জায়গায় একটা ছোট মন্দির, জায়গাটা পাড়াগাঁ-মত, অনেক মেয়েরা জড়ো হয়েছে, কি পুজো হচ্চে। আমি মন্দির দেখে সেখানে দাঁড়িয়ে গেলাম–দেবতার স্থানে পূজা-অর্চনা হতে দেখলে আমার বড় কৌতূহল হয় দেখবার ও জানবার জন্যে। একটা বড় বটগাছের তলায় ছোট্ট মন্দিরটা, বটের ঝুরি ও শেকড়ের দৃঢ় বন্ধনে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা–মন্দিরের মধ্যে সিঁদুর মাখানো গোল গোল পাথর, ছোট একটা পেতলের মূর্তিও আছে। শুনলাম ষষ্ঠীদেবীর মূর্তি। বাড়ি থেকে মেয়েরা নৈবিদ্যি সাজিয়ে এনেচে, পুরুত ঠাকুর পুজো করে সকলকে। ফুলবেলপাতা নির্মাল্য দিলেন–ছেলেমেয়েদের মাথায় শান্তিজল ছিটিয়ে দিলেন। সবাই সাধ্যানুসারে কিছু কিছু দক্ষিণা দিলে পুরুত ঠাকুরকে, তারপর নিজের নিজের ছেলেমেয়েদের নিয়ে, নৈবিদ্যির খালি থালা হাতে সবাই বাড়ি চলে গেল। কাছেই একটা পুকুর, পুরুত ঠাকুর আমার হাতেও দুখানা বাতাসা ও ফুলবেলপাতা দিয়েছিলেন–বাতাসা দুখানা খেয়ে পুকুরে জল খেলাম-ফুলবেলপাতা পকেটে রেখে দিলাম। ছোট্ট গ্রামখানা– দূরে রেলের লাইন, ভাঙা পুকুরের ঘাটটা নির্জন, চারিধারেই বড় বড় গাছে ঘেরা শান্ত, স্তব্ধ অপরা–অনেক দিন পরে এই পুজোর ব্যাপারটা, বিশেষ করে মেয়েদের মুখে একটা ভক্তির ভাব, পুজোর মধ্যে একটা অনাড়ম্বর সারল্য আমার ভাল লাগল।
হাওড়া-পুল পার হয়েচি, এক জায়গায় একজন ভিখারিণী আধ-অন্ধকারের মধ্যে। চেঁচিয়ে কার সঙ্গে ঝগড়া করছে আর কাঁদছে। কাছে গিয়ে দেখলাম ভিখারিণী অন্ধ, বেশ ফর্সা রং, হিন্দুস্থানী–বৃদ্ধা না হলেও প্রৌঢ়া বটে। তার সামনে একখানা ময়লা ন্যাকড়া পাতা–সেটাতে একটা পয়সাও নেই–গোটা-দুই টিনের কালো তোবড়া মগ, একটা ময়লা পুঁটুলি, একটা ভাঁড়–এই নিয়ে তার কারবার। সে একটা সাত-আট বছরের মেয়ের সঙ্গে ঝগড়া করচে–হিন্দীতে বলচে–তুই অমন ক’রে মারবি কেন? তোকে আমি ভিক্ষে করে খাইয়ে এত বড়টা করলাম আর তুই আমাকেই মার দিতে শুরু করলি–আমার কপাল পোড়া, নইলে নিজের পেটের সন্তান এমন বদ হবে কেন? দ্যাখ দেখি কি দিয়ে মারলি, কপালটা কেটে গেছে–
মেয়েটা হি-হি করে হাসচে এবং কৌতুকের সঙ্গে রাস্তা থেকে ধুলোবালি খোয়া কুড়িয়ে ছুঁড়ে ছুঁড়ে মাকে মারছে।
আমি মেয়েটাকে একটা কড়া ধমক দিয়ে বললাম–ফের মাকে যদি অমন করবি, তবে পুলিসে ধরিয়ে দেবো। পকেটে হাত দিয়ে দেখি, আনা সাতেক পয়সা আছে–সেগুলো সব তার ময়লা নেকড়াখানায় রেখে দিয়ে বললুম–তুমি কেঁদো না বাছা–আমি কাল এসে তোমায় আরও পয়সা দেবো। তোমার মেয়ে আর মারবে না। যদি মারে তো বলে দিও, কাল আমি দেখে নেবো–
এমন ছন্নছাড়া করুণ দুরবস্থার রূপ জীবনে কোনদিন দেখিনি। পরদিন হাওড়া-পুলে গিয়েছিলাম কিন্তু সেদিন বা আর কোনদিন সেই অন্ধ ভিখারিণীর দেখা পাইনি। তাকে কত খুঁজেছি, ভগবান জানেন। প্রতিদিন শোবার আগে তার কথা আমার মনে হয়।
মনে মনে বলি, আটঘরার বটতলায় তোমায় প্রথম দেখেছিলুম ঠাকুর, তোমার মুখে অত করুণা মাখানো, মানুষকে এত কষ্ট দাও কেন? তা হবে না, তার ভাল করতেই হবে তোমায়, তোমার আশীর্বাদের পুণ্যধারায় তার সকল দুঃখ ধুয়ে ফেলতে হবে তোমাকে।
এর মধ্যে একদিন কালীঘাটের মন্দিরে গেলুম।
সেদিন বেজায় ভিড়–কি একটা তিথি উপলক্ষে মেলা যাত্রী এসেচে। মেয়েরা পিষে যাচ্ছে ভিড়ের মধ্যে অথচ কেউ ওদের সুবিধে-অসুবিধে দেখবার নেই। আমার সামনেই একটি তরুণী বধূ হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল–আমি একজন প্রৌঢ়া বিধবাকে বললাম– গেল, গেল, ও মেয়েটির হাত ধরে তুলুন–। কাদামাখা কাপড়ে বধূটি দিশাহারা ভাবে উঠে দাঁড়াল, আমি তার সঙ্গের লোকদের খোঁজ নিয়ে ভিড়ের ভেতর থেকে অতিকষ্টে খুঁজে বার করলাম–ভিড়ের দ্বারা চালিত হয়ে তারা অনেকদূর গিয়ে পড়েছিল। এত করেও অনেকেরই দেবদর্শন ঘটল না, পাণ্ডারা সকলকে মন্দিরে ঢুকতে দিচ্ছে না শুনলুম, কেন তা জানিনে। মেয়েদের দুঃখ দেখে আমার নিজের ঠাকুর দেখার ইচ্ছে আর রইল না।
আষাঢ় মাসের শেষ দিন। বৈকালের দিকটা মেজবাবু মোটরে বেরিয়ে গিয়েছিলেন, বেলা পাঁচটার সময় ফিরে এসে আমায় হিসেবের খাতা দেখাতে ডেকে পাঠালেন। রোজ তিনি দুপুরের পরে আপিসে বসে খাতা সই করেন, আজ তিনি ছিলেন না। মেজবাবুকে খাতা দেখানো বড় মুশকিলের ব্যাপার, আবার মেজবাবুকে আমার একটু ভয় হয়, তার ওপরে তিনি প্রত্যেক খরচের খুঁটিনাটি কৈফিয়ৎ চাইবেন। খাতা দেখতে দেখতে মুখ না তুলেই বললেন–তামাকওয়ালার ভাউচার কোথায়?
আমি বললাম–তামাকওয়ালা ভাউচার দেয়নি। খুচরা দোকান–ওরা ভাউচার রাখে না–
মেজবাবু ভ্রূ কুঁচকে বললেন–কেন, নবীন মুহুরী তো ভাউচার আনতো?
তাঁর মুখ দেখে মনে হ’ল তিনি আমায় অবিশ্বাস করচেন। আমি জানি নবীন মুহুরী যেখানে ভাউচার মেলে না–মনিবকে বুঝিয়ে দেবার জন্যে সেখানে ভাউচার নিজেই বানাতো। আমি সে মিথ্যার আশ্রয় নিই না। বললাম–আপনি জেনে দেখবেন ওরা ভাউচার কখনো দেয় না। আমি এসে পর্যন্ত তো দেখচি—
আমি যেখানে দাঁড়িয়ে কথা বলচি, তার সামনেই বড় জানালা–তার ঠিক ওপরে– মেজবাবুর অফিসের সামনাসামনি একটা শানবাঁধানো চাতাল। অন্দরমহলের একটা দোর দিয়ে চাতালটায় আসা যায় বলে জানালায় প্রায়ই পরদা টাঙানো থাকে। আজ সেটা গোটানো ছিল।
আমি একবার মুখ তুলতেই জানালা দিয়ে নজর পড়ল অন্দরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কাদের ছোট্ট একটি খোকা, নিতান্ত ছোট, বছর দুই বয়স হবে। বোধ হ’ল যেন দরজা খোলা না পেয়ে চুপ ক’রে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। আমি ভাবছি, বেশ খোকাটি তো, কাদের খোকা? এ বাড়িতে যতদূর জানি অত ছোট ছেলে কারুর তো নেই? এ ওখানে এল কার সঙ্গে?
মেজবাবু বললেন–এদিকে মন দাও, ওদিকে কি দেখচ?
আমি বললাম–কাদের খোকা দাঁড়িয়ে রয়েচে ওখানে–আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললাম–ওই যে দাঁড়িয়ে রয়েচে চাতালের দরজায়, বাড়িতে ঢুকতে পাচ্ছে না বোধ হয়।
মেজবাবু সেদিকে চেয়ে বললেন–কই? কোথায় কে?
ঠিক সেই সময় অন্দরের দরজা খুলে মেজবাবুর স্ত্রী তাঁকে অনেকবার মোটরে উঠতে নামতে দেখেচি বার হয়ে এলেন এবং খোকাকে কোলে তুলে নিলেন। আমি চোখ নামিয়ে নিলাম। মেজবাবু বললেন–কোথায় তোমার খোকা না কি?
আমি বিস্মিত হয়ে বললাম–বা রে, ওই তো উনি খোকাকে কোলে নিলেন!
চোখ তুলে চাতালের দিকে চেয়ে মেজবাবুর স্ত্রীকে আর দেখতে পেলাম না, অন্দরের দরজাও বন্ধ, নিয়ে বোধ হয় বাড়ির মধ্যে চলে গিয়েচেন। মেজবাবু বললেন–কে নিয়ে গেলেন? উনি মানে কি? কি বকচ পাগলের মত!…
মেজবাবু আমার দিকে কেমন এক ধরনের চেয়ে রয়েচেন দেখলাম। আমি তাঁর সে দৃষ্টির সামনে থতমত খেয়ে গেলাম–আমার মনে হ’ল মেজবাবু সন্দেহ করচেন আমার মাথা খারাপ আছে নাকি? সঙ্গে সঙ্গে বিস্মিত হলাম একথা ভেবে যে এই ওঁর স্ত্রী দরজা খুলে এলেন, খোকাকে কোলে তুলে নিলেন, এই তো দিনমানে আর এই ত্রিশ হাতের মধ্যে চাতাল, এ উনি দেখতে পেলেন না কেন? পরক্ষণেই চট করে আমার সন্দেহ হ’ল আমার সেই পুরানো রোগের ব্যাপার এর মধ্যে কিছু আছে নাকি? এত সাধারণ ও স্বাভাবিক ঘটনার মধ্যে যে অন্য কিছু আছে বা হতে পারে, এ এতক্ষণ আমার মনেই ওঠেনি। তা হলে কোনো কথা কি বলতাম? এক্ষুনি চাকুরি থেকে ছাড়িয়ে দিতে পারে। বলতেই পারে, এর মাথা খারাপ, একে দিয়ে চলবে না।
কিন্তু আমার বড় কৌতূহল হ’ল। সন্ধ্যার সময় মোহিনী ঝি আমার বারান্দার সামনে দিয়ে যাচ্চে, তাকে জিজ্ঞেস করলুম–শোন, আচ্ছা বাড়িতে দেড় বছর দু’বছরের খোকা কার আছে বল তো? ঝি বললে–এত ছোট খোকা তো কারুর নেই।
সেইদিন রাত বারোটায় খুব হৈ-চৈ। মেজবাবুর স্ত্রীর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন, লোক ছুটলো ডাক্তার আনতে। মেজবাবুর স্ত্রী যে অন্তঃসত্বা ছিলেন বা সন্ধ্যার পর থেকে পাস-করা ধাত্রী এসে বসে আছে, এ-সব কথা তখন আমি শুনলাম। কারণ সবাই বলাবলি করচে। শেষরাত্রে শুনলাম তাঁর একটি পুত্রসন্তান হয়েছে।
মনে মনে বিস্মিত হ’লেও কারও কাছে এ নিয়ে আর কোন কথা বললাম না। নিজেই দেখি, অথচ নিজেই বুঝিনে এ-সবের মানে কি। চুপচাপ থাকাই আমার পক্ষে ভাল।
এই ঘটনার পরে আমার ভয় হ’ল আমার সেই রোগ আবার আরম্ভ হবে। ও যখন আসে তখন উপরি-উপরি অনেক বার হয়–তারপর দিনকতকের জন্যে আবার একেবারেই বন্ধ থাকে। এই বার বেশী করে শুরু হলে আমার চাকুরি ঘুচে যাবে– সীতার কোন কিনারাই করতে পারব না।
মেজবাবু হিসেবের খাতা লেখার কাজ দিলেন নবীন মুহুরীকে। তার ফলে আমার কাজ বেজায় বেড়ে গেল–ঘুরে ঘুরে এঁদের কাজে খিদিরপুর, বরানগর, কালীঘাট করতে হয়– আর দিনের মধ্যে সতের বার দোকানে বাজারে যেতে হয় চাকরকে সঙ্গে নিয়ে। খাওয়া দাওয়ার নির্দিষ্ট সময় নেই, দিনে রাতে শুধু ছুটোছুটির কাজ। এই দোকানের হিসেব নবীন মুহুরীকে বুঝিয়ে দেওয়া একটা ঝঞ্ঝাট–রোজ সে আমাকে অপমান করে ছুতোয় নাতায়, আমার কথা বিশ্বাস করে না, চাকরদের জিজ্ঞেস করে আড়ালে সত্যি সত্যি কি দরে জিনিসটি এনেচি। সীতার মুখ মনে করে সবই সহ্য করে থাকি।
কার্তিক মাসে ওদের দেশের সেই মহোৎসব হবে–আমাদের সকলকে দেশে পাঠানো হ’ল। আমি অনেক আগে থেকেই শুনে আসচি–অত্যন্ত কৌতূহল ছিল দেখবো ওদের সাম্প্রদায়িক ধর্মানুষ্ঠান কি রকম।
গ্রামে এঁদের প্রকাণ্ড বাড়ি, বাগান, দীঘি, এঁরাই গ্রামের জমিদার। তবে বছরে এই একবার ছাড়া আর কখনও দেশে আসেন না। কুঞ্জ নায়েব বাকী দশ মাস এখানকার মালিক।
একটা খুব বড় ফাঁকা মাঠে মেলা বসেছে–এখানকার দোকান-পসারই বেশী। অনেকগুলো খাবারের দোকান, মাটির খেলনার দোকান, মাদুরের দোকান।
একটা বড় বটগাছের তলাটা বাঁধানো, সেটাই নাকি পীঠস্থান। লোকে এসে সেইখানে পুজো দেয়–আর বটগাছটার ডালে ও ঝুরিতে ইঁট বাঁধা ও লাল নীল নেকড়া বাঁধা। লোকে মানত করার সময় ওই সব গাছের গায়ে বেঁধে রেখে যায়, মানত শোধ দেওয়ার সময় সে খুলে দিয়ে পুজো দেয়। বটতলায় সারি সারি লোক ধর্ণা দিয়ে শুয়ে আছে, মেয়েদের ও পুরুষদের ধর্ণা দেওয়ার জায়গা আলাদা আলাদা।
বড়বাবু ও মেজবাবুকে মোহন্তের গদিতে বসেন–কত্তা নীলাম্বর রায় আসেননি, তাঁর শরীর সুস্থ নয়। এঁদের বেদীর ওপরে আশপাশে তাকিয়া, ফুল দিয়ে সাজানো, সামনে ঝকঝকে প্রকাণ্ড রূপোর থালাতে দিন-রাত প্রণামী পড়চে। দুটো থালা আছে–একটাতে মোহন্তের নজর, আর একটাতে মানত ও পুজোর প্রণামী।
নবীন মুহুরী, বেচারাম ও আমার কাজ হচ্ছে এই সব টাকাকড়ির হিসেব রাখা। এর আবার নানা রকম রেট আছে, যেমন–পাঁচ সিকার মানত থাকলে গদীর নজর একটাকা, তিন টাকার মানতে দু-টাকা ইত্যাদি। কেউ কম না দেয় সেটা মুহুরীদের দেখে নিতে হবে, কারণ মোহন্তরা টাকাকড়ির সম্বন্ধে কথা বলবেন না।
কাজের ফাঁকে আমি বেড়িয়ে দেখতে লাগলাম চারিধার। সবারই সঙ্গে মিশে এদের ধর্মমতটা ভাল করে বুঝবার আগ্রহে যাদের ভাল লাগে তাদেরই নানা কথা জিজ্ঞেস করি, আলাপ করে তাদের জীবনটা বুঝবার চেষ্টা করি।
কি অদ্ভুত ধর্মবিশ্বাস মানুষের তাই ভেবে অবাক হয়ে যাই। কতদূর থেকে যে লোক এসেচে পোঁটলাপুঁটলি বেঁধে, ছেলেমেয়ে সঙ্গে নিয়েও এসেছে অনেকে। এখানে থাকবার জায়গা নেই, বড় একটা মাঠে লোকে এখানে-ওখানে এই কার্তিক মাসের হিমে চট, শতরঞ্জি, হোগলা, মাদুর যে যা সংগ্রহ করতে পেরেছে তাই দিয়ে থাকবার জায়গা তৈরি ক’রে তারই তলায় আছে–কেউ বা আছে শুধু গাছতলাতে। যে যেখানে পারে মাটি খুঁড়ে কি মাটির ঢেলা দিয়ে উনুন বানিয়ে রান্না করচে। একটা সজনে গাছতলায় এক বুড়ী রান্না করছিল–সে একাই এসেচে হুগলী জেলার কোন গাঁ থেকে। তার এক নাতি হুগলীর এক উকিলের বাসার চাকর, তার ছুটি নেই, বুড়ী প্রতি বছর একা আসে।
আমায় বললে–বড্ড জাগ্রত ঠাকুর গো বটতলার গোসাঁই। মোর মালসি গাছে কাঁটাল মোটে ধরতো নি, জালি পড়ে আর খসে খসে যায়। তাই বন্নু বাবার থানে কাঁটাল দিয়ে আসবো, হে ঠাকুর কাঁটাল যেন হয়। বললে না পেত্যয় যাবে, ছোটয়-বড়য় এ-বছর সতেরো গণ্ডা এঁচড় ধরেচে গোসাঁইয়ের কিরপায়।
আর এক জায়গায় খেজুরডালের কুঁড়েতে একটি বৌ বসে রাঁধচে। আর তার স্বামী কুঁড়ের বাইরে বসে খোল বাজিয়ে গান করচে। কাছে যেতেই বসতে বললে। তারা জাতে কৈবর্ত, বাড়ি খুলনা জেলায়, পুরুষটির বয়স বছর চল্লিশ হবে। তাদের ছোট্ট একটি ছেলে মায়ের কাছে বসে আছে, তারই মাথার চুল দিতে এসেচে।
পুরুষটির নাম নিমচাঁদ মণ্ডল। স্বামী-স্ত্রী দু-জনেই বড় ভক্ত। নিমচাঁদ আমার হাতে একখানা বই দিয়ে বললে–পড়ে শোনাও তো বাবু, দু-আনা দিয়ে মেলা থেকে কাল কেনলাম একখানা। বইখানার নাম বটতলার কীর্তন। স্থানীয় ঠাকুরের মাহাত্ম্যসূচক তাতে অনেকগুলো ছড়া। বটতলার গোসাঁই ব্রহ্মার সঙ্গে পরামর্শ করে এখানে এসে আস্তানা বেঁধেচেন, কলিরাজ ভয়ে তাঁর সঙ্গে এই সন্ধি করলে যে বটতলার হাওয়া যত দূর যাবে ততদূর পর্যন্ত কলির অধিকার থাকবে না। বটতলার গোসাঁই পাপীর মুক্তিদাতা, সর্ব জীবের আশ্রয়, সাক্ষাৎ শ্রীহরির একাদশ অবতার।
কলিতে নতুন রূপ শুন মন দিয়া
বটতলে স্থিতি হৈল ভক্তদল নিয়া
খেদে কহে কলিরাজ,
এ বড় বিষম কাজমোর দশা কি হবে গোসাঁই?
ঠাকুর কহিলা হেসে,
মনে না করিহ ক্লেশে থান ত্যজি কোথাও না যাই।
শ্রীদাম সুবল সনে হেথায় আসিব
বট্মূলে বৃন্দাবন সৃষ্টি করি নিব।
নিমচাঁদ শুনতে শুনতে ভক্তিগদগদকণ্ঠে বললে–আহা! আহা! বাবার কত লীলাখেলা!
তার স্ত্রীও কুঁড়ের দোরগোড়ায় এসে বসে শুনচে। মানে বুঝলাম এরা নিজেরা পড়তে পারে না, বইপড়া শোনার আনন্দ এদের কাছে বড় নতুন, তা আবার যাঁর ওরা ভক্ত, সেই বটতলার গোসাঁই সম্বন্ধে বই।
নিমচাঁদ বললে–আচ্ছা, বটতলার হাওয়া কত দূর যায় দা-ঠাকুর?
–কেন বল তো?
—এই যে বলচে কলির অধিকার নেই ওর মধ্যি, তা কত দূর তাই শুধুচ্চি।
—কত দূর আর, ধর আধ ক্রোশ বড়জোর—
নিমচাঁদ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে কি ভেবে বললে–কি করবো দা-ঠাকুর, দেশে লাঙল-গরু করে ফেলেচি, কুড়ো-দুই জমিতে এবার বাগুন রুইয়ে রেখে এসেচি–নয়ত এ বাবার থান ত বিন্দাবন, আপনি পড়লেন–এ স্বগগো ছেড়ে বিলির মোষের মত বিলি ফিরে যাই দা-ঠাকুর? কি বলিস রে তুই, সরে আয় না এদিকে, দা-ঠাকুরকে লজ্জা কি, উনি তো ছেলেমানুষ।
নিমচাঁদের স্ত্রী গলার সুরকে খুব সংযত ও মিষ্টি করে, অপরিচিত পুরুষমানুষের সামনে কথা বলতে গেলে মেয়েরা যেমন সুরে কথা বলে তেমনি ভাবে বললে–হ্যাঁ ঠিকই তো। বাবার চরণের তলা ছেড়ে কোথাও কি যেতে ইচ্ছে করে?
নিমচাঁদ বললে–দু-মণ কোষ্টা ছিল ঘরে, তা বলি বিক্রী করে চল বাবার থানে বাবার ছিচরণ দর্শন করে আসি আর অমনি গঙ্গাছেনটাও সারবো। টাকা বাবা যোগাবেন, সেজন্য ভাবিনে। ওরে শোন, কাল তুই তো ধন্না দিবি সকালে, আজ রাতে ভাতে জল দিয়ে রেখে দিস–
জিজ্ঞেস করে জানলাম ছেলের অসুখের জন্যে ধর্ণা দেবার ইচ্ছে আছে ওদের।
নিমচাঁদের বৌ বললে–বুঝলেন দাদাঠাকুর, খোকার মামা ওর মুখ দেখে তিনটে টাকা দিলে খোকার হাতে। তখন পয়সার বড় কষ্ট যাচ্চে, কোষ্টা তখন জলে, কাচলি তো পয়সা ঘরে আসবে? তো বলি, না, এ টাকা খরচ করা হবে না। এ রইল তোলা বাবার থানের জন্যি। মোহন্ত বাবার গদীতে দিয়ে আসব।
সেই দিন বিকেলে নিমচাঁদ ও তাঁর বৌ পুজো দিতে এল গদীতে। নবীন মুহুরী তাদের কাছে রেট-মত প্রণামী ও পুজোর খরচ আদায় করলে অবিশ্যি–তা ছাড়া নিমচাঁদের বৌ নিজের হাতে সেই তিনটে টাকা বড়বাবুর সামনের রূপোর থালায় রেখে দিয়ে বড়বাবুর পায়ের ধুলো নিয়ে কোলের খোকার মাথায় মুখে দিয়ে দিলে।
তার পর সে একবার চোখ তুলে মোহন্তদের দিকে চাইলে এবং এদের ঐশ্বর্যের ঘটাতেই সম্ভবত অবাক হয়ে গেল–বুদ্ধিহীন চোখে শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের সঙ্গে টাকা-পয়সাতে পরিপূর্ণ ঝকঝকে রূপোর থালাটার দিকে বার-কতক চাইলে, রঙীন শালু ও গাঁদাফুলের মালায় মোড়া থামগুলোর দিকে চাইলে–জীবনে এই প্রথম সে গোসাঁইয়ের থানে এসেছে, সব দেখেশুনে লোকের ভিড়ে, মোহন্ত মহারাজের আড়ম্বরে, অনবরত বর্ষণরত প্রণামীর ঝমঝমানি আওয়াজে সে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেল। কতক্ষণ হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইল, বাইরে থেকে ক্রমাগত লোক ঢুকচে, তাকে ক্রমশ ঠেলে একধারে সরিয়ে দিচ্চে, তবুও সে দাঁড়িয়েই আছে।
ওকে কে একজন ঠেলা দিয়ে এগিয়ে আসতে গেল, আমি ওর দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারিনি। ওর মুখচোখের মুগ্ধ ভক্তিস্তব্ধ দৃষ্টি আমায়ও মুগ্ধ করেছে–এ এক নতুন অভিজ্ঞতা আমার জীবনের, এই বাজে শালুর বাহার আর লোকের হৈচৈ আর মেজবাবু, বড়বাবুর চশমামণ্ডিত দাম্ভিক মুখ দেখে এত ভাব ও ভক্তি আসে!–যে ঠেলা দিয়ে এদিকে আসছিল, আমি তাকে ধমক দিলুম। তার পর ওর চমক ভাঙতে ফিরে বাইরে বেরিয়ে গেল।
ওরা চলে গেলে একটি বৃদ্ধা এল, তার বয়স অনেক হয়েছে, বয়সে গলার সুর কেঁপে গিয়েচে, হাত কাঁপচে, সে তার আঁচল থেকে একটি আধুলি খুলে থালায় দিতে গেল। নবীন মুহুরী বললে–রও গো, রাখ––আধুলি কিসের?
বুড়ী বললে–এই-ই ঠাকুরের মা-ন-ত শো-ধে-র পে-র-ণা-মী–
নবীন মুহুরী বললে–পাঁচ সিকের কমে ভোগের পুজো নেই–পাঁচ সিকিতে এক টাকা গদীর নজর–
বুড়ী শুনতে পায় না, বললে–কত?
নবীন আঙুল দেখিয়ে চেঁচিয়ে বললে–এক টাকা—
বুড়ী বললে–আর নেই, মা-দু-র কি-নে-লা-ম ছ-আ-না-র, আ-র—
নবীন মুহুরী আধুলি ফেরত দিয়ে বললে–নিয়ে যাও, হবে না। আর আট আনা নিয়ে এস—
বড়বাবু একটা কথাও বললেন না। বুড়ী কাঁপতে কাঁপতে ফিরে গেল এবং ঘণ্টাখানেক পর সিকিতে, দু আনিতে, পয়সাতে একটা টাকা নিয়ে এসে প্রণামী থালায় রাখল।
ওরা চলে গেলে আমার মনে হ’ল এই সরল, পরম বিশ্বাসী পল্লীবধূ, এই বৃদ্ধা ওদের কষ্টার্জিত অর্থ কাকে দিয়ে গেল–মেজবাবুকে, বড়বাবুকে? এই এত লোক এখানে এসেছে, এরা সবাই চাষী গরীব গৃহস্থ, কি বিশ্বাসে এখানে এসেছে জানি নে–কিন্তু অম্লানবদনে খুশীর সঙ্গে এদের টাকা দিয়ে যাচ্চে কেন? এই টাকায় কলকাতায় ওঁদের স্ত্রীরা গহনা পরবেন, মোটরে চড়বেন, থিয়েটার দেখবেন, ওঁরা মামলা করবেন, বড়মানুষি সাহেবিয়ানা করবেন–ছোটবাবু বন্ধুবান্ধব নিয়ে গানবাজনার মজলিশে চপ-কাটলেট ওড়াবেন, সেই জন্যে?
পরদিন সকালে দেখলাম নিমচাঁদের স্ত্রী পুকুরে স্নান করে সারাপথ সাষ্টাঙ্গ নমস্কার করতে করতে ধুলোকাদা-মাখা গায়ে বটতলায় ধর্ণা দিতে চলেচে–আর নিমচাঁদ ছেলে কোলে নিয়ে ছলছল চোখে তার পাশে পাশে চলেচে।
সেই দিন রাত্রে শুনলাম মেলায় কলেরা দেখা দিয়েছে। পরদিন দুপুরবেলা দেখি বটতলার সামনের মাঠটা প্রায় ফাঁকা হয়ে গিয়েছে, অনেকেই পালিয়েছে। নিমচাঁদের কুঁড়েঘরের কাছে এসে দেখি নিমচাঁদের স্ত্রী বসে–আমায় দেখে কেঁদে উঠল। নিমচাঁদের কলেরা হয়েচে কাল রাত্রে–মেলার যারা তদারক করে, তারা ওকে কোথায় নাকি নিয়ে যেতে চেয়েচে, মাঠের ওদিকে কোথায়। আমি ঘরে ঢুকে দেখি নিমচাঁদ ছটফট করছে, খুব ঘামচে।
নিমচাঁদের স্ত্রী কেঁদে বললে–কি করি দাদাঠাকুর, হাতে শুধু যাবার ভাড়াটা আছে–কি করি কোথা থেকে–
মেজবাবুকে কথাটা বললাম গিয়ে, তিনি বললেন–লোক পাঠিয়ে দিচ্চি, ওকে সিগ্রিগেশন ক্যাম্পে নিয়ে যাও–মেলার ডাক্তার আছে সে দেখবে–
নিমচাঁদের বৌ-এর কি কান্না ওকে নিয়ে যাবার সময়। আমরা বোঝালুম অনেক। ডাক্তার ইনজেকশন দিলে। মাঠের মধ্যে মাদুর দিয়ে সিগ্রিগেশন ক্যাম্প করা হয়েছে– অতি নোংরা বন্দোবস্ত। সেখানে সেবাশুশ্রষার কোন ব্যবস্থাই নেই। ভাবলুম চাকুরি যায় যাবে, ওকে বাঁচিয়ে তুলব, অন্তত বিনা তদারকে ওকে মরতে দেবো না। সারারাত জেগে রোগীকে দেখাশুনা করলুম একা। সিগ্রিগেশন ক্যাম্পে আরও চারটি রোগী এল–তিনটে সন্ধ্যার মধ্যেই মরে গেল। মেলার ডাক্তার অবিশ্যি নিয়ম-মত দেখলে। এদের পয়সা নিয়ে যারা বড়-মানুষ, তারা চোখে এসে দেখেও গেল না কাউকে। রাত্রিটা কোনরকমে কাটিয়ে বেলা উঠলে নিমচাঁদও মারা গেল। সে এক অতি করুণ ব্যাপার! ওদের দেশের লোক খুঁজে বার করে নিমচাঁদের সৎকারের ব্যবস্থা করা গেল। নিমচাঁদের স্ত্রীর দিকে আমি আর চাইতে পারি নে–বটতলায় ধর্ণা দেওয়ার দিন থেকে সেই যে সে উপবাস করে আছে, গোলমালে আর তার খাওয়াই হয়নি। রুক্ষ চুল একমাথা, সেই ধূলিধূসরিত কাপড়–খবর পেয়ে সে ধর্ণা ফেলে বটতলা থেকে উঠে এসেছে–চোখ কেঁদে কেঁদে লাল হয়েছে, যেন পাগলীর মত দৃষ্টি চোখে। এখন আর সে কাঁদছে না, শুধু কাঠের মত বসে আছে, কথাও বলে না, কোন দিকে চায় না।
মেজবাবুকে বলাতে তিনি ওকে দেশে পাঠিয়ে দেওয়ার খরচ দু-টাকা মঞ্জুর করলেন। কিন্তু সে আমি যথেষ্ট বললাম ও অনুরোধ করলাম ব’লে। আরও কত যাত্রী এ-রকম মরে গেল বা তাদের কি ব্যবস্থা হ’ল এ-সব দেখবার দায়িত্ব এদেরই তো। ওরাই রইল নির্বিকার ভাবে বসে। আমার কাছে কিছু ছিল, যাবার সময় নিমচাঁদের স্ত্রীর হাতে দিলুম। চোখের জল রাখতে পারি নে, যখন সে চলে গেল।
দিন-দুই পরে রাত্রে বসে আমি ও নবীন মুহুরী হিসেব মেলাচ্চি মেলার দেনা-পাওনার। বেশ জ্যোৎস্না রাত, কার্তিকের সংক্রান্তিতে পরশু মেলা শেষ হয়ে গিয়েছে, বেশ শীত আজ রাত্রে।
এমন সময় হঠাৎ আমার কি হ’ল বলতে পারিনে–দেখতে দেখতে নবীন মুহুরী, মেলার আটচালা ঘর, সব যেন মিলিয়ে গেল। আমি যেন এক বিবাহ-সভায় উপস্থিত হয়েছি–অবাক হয়ে চেয়ে দেখি সীতার বিবাহ-সভা। জ্যাঠামশায় কন্যাসম্প্রদান করতে বসেছেন, খুব বেশী লোকজনের নিয়ন্ত্রণ হয়নি, বরপক্ষেও বরযাত্রী বেশী নেই। দাদাকেও দেখলুম–দাদা ব’সে ময়দা ঠাসচে ..আরও সব কি কি…ঘষা কাঁচের মধ্যে দিয়ে যেন সবটা দেখচি–খানিকটা স্পষ্ট, খানিকটা অস্পষ্ট।
চমক ভাঙলে দেখি নবীন মুহুরী আমার মাথায় জল দিচ্চে। বললে–কি হয়েছে। তোমার, মাঝে মাঝে ফিট হয় না-কি?
আমি চোখ মুছে বললুম–না। ও কিছু না–
আমার তখন কথা বলতে ভাল লাগছে না। সীতার বিবাহ নিশ্চয়ই হচ্চে, আজ এখুনি হচ্ছে। আমি ওকে বড় ভালবাসি–আমার চোখকে ফাঁকি দিয়ে জ্যাঠামশায় ওর বিবাহ দিতে পারবেন না। আমি সব দেখেচি।
নবীন মুহুরীকে বললাম–তুমি আমাকে ছুটি দাও আজ, শরীরটা ভাল নেই, একটু শোব।
পরদিন বড়বাবুর চাকর কলকাতা থেকে এল। মায়ের একখানা চিঠি কলকাতার ঠিকানায় এসে পড়ে ছিল, মায়ের জবানি জ্যাঠামশায়ের লেখা আসলে। ২রা অগ্রহায়ণ সীতার বিয়ে, সেই জ্যাঠামশায়ের ঠিক করা পাত্রের সঙ্গেই। তিনি কথা দিয়েছেন, কথা খোয়াতে পারেন না। বিশেষ, অত বড় মেয়ে ঘরে রেখে পাঁচজনের কথা সহ্য করতে প্রস্তুত নন। আমরা কোন কালে কি করব তার আশায় তিনি কতকাল বসে থাকেন– ইত্যাদি।
বেচারী সীতা! ওর সাবান মাখা, চুলবাঁধা, মিথ্যে শৌখীনতার অক্ষম চেষ্টা মনে পড়ল। কত করে ওর মুখের দিকে চেয়ে এত কাল কিছু গ্রাহ্য করিনি। বেশ দেখতে পেলাম ওর ঘন কালো চুলের সিঁতিপাটি ব্যর্থ হয়ে গেল––ওর শুভ্র, নিষ্পাপ জীবন নিয়ে সবাই ছিনিমিনি খেললে।