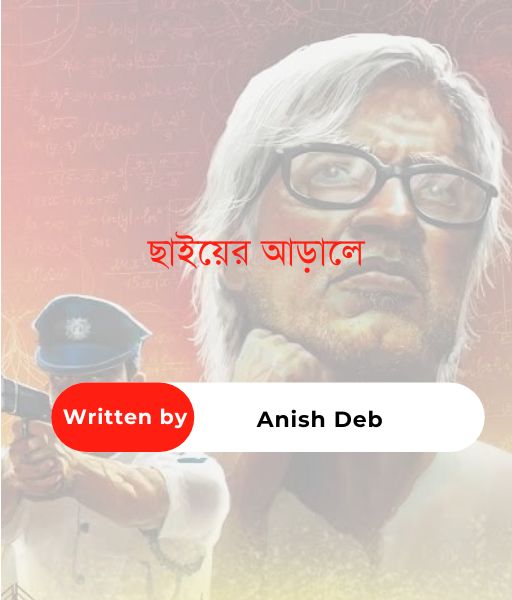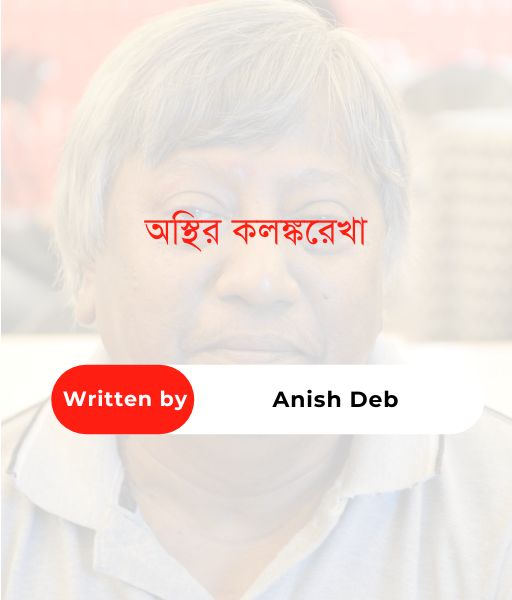একজনের ভেতরে দুজন
অজয়কে নিয়ে কখনও গল্প লিখব ভাবিনি৷ কিন্তু গতকাল সন্ধেবেলার একটা ঘটনায় অজয় মনের সামনে চলে এল৷ সময়ের গাড়ি এক ঝটকায় আমাকে উড়িয়ে নিয়ে গেল পঞ্চাশ বছর পেছনে৷ আমি পৌঁছে গেলাম আমার স্কুলে৷ ক্লাস সেভেনের ‘সি’ সেকশানের ক্লাসরুমে৷ কতই বা বয়েস তখন আমার? সত্যি-সত্যি ‘বাও কি তেও—মা বলেছে আও কম’৷
অজয় আমার সহপাঠী ছিল, কিন্তু বন্ধু ছিল না৷ সত্যি বলতে কী, গোটা ক্লাসে অজয়ের কোনও বন্ধু ছিল না৷ ও ছিল একা, কিন্তু দ্রষ্টব্য৷ ও নানান ঢঙে বিচিত্র সব দুষ্টুমি পারফর্ম করত৷ আর আমরা, ক্লাস সেভেনের বাকি আটত্রিশ কি উনচল্লিশ জন, অজয়ের পারফরম্যান্স অবাক হয়ে দেখতাম৷ অজয় ছিল বলতে গেলে ‘হিরো’৷ আমরা ছিলাম নীরব দর্শক৷
অজয়ের কথা লিখতে গিয়ে ওর মুখটা ভেসে উঠছে চোখের সামনে৷
গোলগাল চেহারা, মাথায় কোঁকড়ানো চুল, চোখে কালো ফ্রেমের চশমা৷ চশমার কাচের আড়ালে দুটো প্রাণবন্ত চঞ্চল চোখ৷ ঠোঁটের ওপরে হালকা গোঁফের রেখা৷
শুধু অজয় কেন, একইসঙ্গে ভেসে উঠছে ক্লাসরুমটাও৷ আমরা সবাই যে-যার ডেস্কের সামনে ছোট-ছোট চেয়ারে বসে আছি৷
আমাদের স্কুলটা ছিল মাঝ-কলকাতার এক বিখ্যাত সরকারি স্কুল৷ ট্রামরাস্তার পাশেই তার বিশাল বিল্ডিং৷ বিল্ডিং-এর লাগোয়া এক প্রকাণ্ড পার্ক৷ পার্কে প্রচুর গাছপালা, এবং তার ঠিক মধ্যিখানে এক মনোরম চৌকো দিঘি৷ সেই বিশাল চৌকো দিঘিকে ঘিরে ছিল বেশ কয়েকটা সাঁতারের ক্লাব৷
আমাদের ক্লাসরুমটা ছিল পার্কের দিকে, দোতলায়৷ লাস্ট পিরিয়ডে ক্লাসরুমের জানলা দিয়েই আমরা দেখতে পেতাম বাচ্চাকাচ্চারা হাত-পা ছুড়ে সাঁতার শিখছে৷
অজয় আমার প্রথম নজর কাড়ে ওর গানের জন্যে৷
একজন টিচার ক্লাস শেষ করে চলে যাওয়ার পর পরের টিচার ক্লাসে ঢুকতে-ঢুকতে দশ কি পনেরো সেকেন্ড সময় পেরিয়ে যেত৷ সেই অবসরটুকুতে আমরা বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে গল্পে মেতে উঠতাম৷ সকলের কথাবার্তা মিলেমিশে গিয়ে এক প্রবল গুঞ্জন তৈরি হয়ে যেত ক্লাসরুমে৷
কিন্তু অজয় সেসবের মধ্যে ছিল না৷ দুটো ক্লাসের মাঝখানের এই ফাঁকটুকুতে ও ডেস্কে তাল ঠুকে গান ধরত৷
না, অজয়ের গানের গলা ছিল না৷ বেসুরো হেঁড়ে গলায় ও গান গাইত৷ দেশাত্মবোধক গান৷ যেমন, ‘ছেড়ে দাও রেশমি চুড়ি বঙ্গনারী কভু হাতে আর পোরো না’, ‘জননী গো লহ তুলে বক্ষে সান্ত্বন বাস দেহ তুলে চক্ষে’, ‘ধনধান্য পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা’৷
কিন্তু স্যার ক্লাসে ঢুকলেই ও চুপ করে যেত৷
ক্লাসে আমি যেখানে বসতাম, আর অজয় যেখানে বসত, এই দুটো জায়গার মধ্যে দূরত্ব ছিল অনেকটাই৷ তাই আমি দূর থেকে আমার সহপাঠীকে লক্ষ করতাম৷ ও সবসময় শক্তি আর ফুর্তিতে টগবগ করত৷ বেশ বুঝতে পারতাম, ঠিকঠাকভাবে লেখাপড়া করার জন্যে ওর জন্ম হয়নি৷
আমাদের সময়ে স্কুলের জানলাগুলো ছিল পুরোনো ধাঁচের৷ কাঠের ফ্রেমে কাচের শার্সি বসানো৷ জানলাটার মোট তিনটে ভাগ৷ জানলার মাঝের অংশটা ছিল ফিক্সড—দেওয়ালের মতো৷ আর তার দু’পাশের দুটো অংশে ছিল দুটো এক পাল্লাওয়ালা জানলা৷ তবে জানলার কোথাও কোনও গরাদ কিংবা গ্রিলের ব্যাপার ছিল না৷ অনেকটা ফ্রেঞ্চ উইন্ডোর মতো৷ আর জানলার বাইরে বেশ চওড়া কার্নিশ৷ ফলে ইচ্ছে করলে কেউ বাইরে থেকে বেয়ে উঠে জানলা দিয়ে ঘরে ঢুকে পড়তে পারে৷
জানলা নিয়ে এত কথা বলার কারণ, অজয়ের কীর্তিকাহিনির প্রথম এপিসোডে জানলার একটা বিশেষ ভূমিকা আছে৷
সকালবেলার প্রথম ক্লাস৷ বাংলার স্যার পীতাম্বরবাবু ক্লাসে ঢুকে গুছিয়ে বসেছেন৷ পোশাক ধপধপে ধুতি আর পাঞ্জাবি৷ রোগা, ফরসা চেহারা৷ চোখে চশমা৷
কয়েকমাস এই স্যারের ক্লাস করার অভিজ্ঞতায় আমরা সকলেই জেনে গেছি এই স্যার বেশ কড়া এবং গম্ভীর প্রকৃতির৷ তাই আমরা ওঁকে নিজেদের মধ্যে ‘ভোম্বল’ নামে ডাকি৷
শুধু তাই নয়, একদিন অঙ্কের স্যার মহাদেববাবুর পিরিয়ডে প্রক্সি দিতে পীতাম্বরবাবু এসেছিলেন৷ এসেই মাপা গলায় বলেছিলেন, ‘অ্যাই, শোনো৷ তোমাদের মধ্যে একজন এখানে এসো৷ এসে একটা গল্প বলো৷ বাকি সবাই মন দিয়ে শুনবে—কেউ কোনও গোলমাল করবে না—৷’
স্যারের কথা শেষ হওয়ামাত্রই অজয় হাত তুলে বলেছিল, ‘আমি গল্প বলব, স্যার?’
‘হ্যাঁ, চলে এসো—৷’
অজয় গম্ভীর মুখে স্যারের খাটো মঞ্চের পাশে গিয়ে দাঁড়াল৷ গম্ভীর গলায় স্যারকে জিগ্যেস করল, ‘স্যার, ‘‘ভোম্বল সর্দার’’ গল্পটা বলব?’’
স্যার ‘হ্যাঁ’ বলার আগেই আমরা গোটা ক্লাস হেসে কুটিপাটি৷ কিন্তু অজয় তখনও গম্ভীর মুখে স্যারের দিকে তাকিয়ে স্যারের অনুমতির অপেক্ষা করছে৷
তো যেদিনের কথা বলছিলাম৷
সকালবেলার প্রথম ক্লাসে এসে পীতাম্বরবাবু রোলকল করতে শুরু করেছেন৷ আমরা রোল নম্বর অনুযায়ী পরপর সাড়া দিচ্ছি : ‘প্রেজেন্ট, স্যার’, ‘ইয়েস স্যার’, ‘প্রেজেন্ট প্লিজ’ ইত্যাদি৷
অজয়ের রোল নম্বর ছিল আঠেরো৷ স্যার ‘এইটিন’ বলে ডাকার সঙ্গে-সঙ্গে কোথা থেকে যেন উত্তর ভেসে এল, ‘প্রেজেন্ট প্লিজ৷’
অজয় যে-ডেস্কে বসত সেইদিকে তাকালেন পীতাম্বরবাবু৷
অজয়ের ডেস্ক-চেয়ার খালি৷
অবাক হয়ে স্যার আবার ডাকলেন, ‘রোল নাম্বার এইটিন—৷’
আবার উত্তর এল, ‘প্রেজেন্ট প্লিজ—৷’
কিন্তু অজয়কে দেখা যাচ্ছে না৷
আমরাও বেশ অবাক হয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে অজয়কে খুঁজে বেড়াচ্ছি, কিন্তু অজয় ক্লাসে কোথাও নেই৷
‘অজয়, তুই কোথায়? শিগগিরই বেরিয়ে আয়—৷’ বেশ উত্তেজিত হয়ে ডেকে উঠলেন পীতাম্বরবাবু৷
উত্তরে এক অদ্ভুত শব্দ ভেসে এল৷ দু-ঠোঁট মুখের ভেতরে ঢুকিয়ে বাতাস টানলে যে বিচিত্র শব্দ তৈরি হয়, সেরকম শব্দ করে কেউ একটা তাল বাজানোর চেষ্টা করছে৷ স্যারের হুঙ্কারে সে-শব্দ মোটেই থামেনি৷
ততক্ষণে আমাদের অনুসন্ধানী চোখ সেই মিউজিশিয়ানকে খুঁজে পেয়েছে৷ সে আর কেউ নয়—আমাদের অজয়৷
একটা জানলার বাইরে কার্নিশে অজয় চিত হয়ে শুয়ে রয়েছে৷ দু-হাঁটু ভাঁজ করা৷ মুখে ওই পিকিউলিয়ার শব্দ করছে, আর হাত দিয়ে নিজের দু-হাঁটুতে তাল ঠুকছে৷
আমরা সবাই মজা পেয়ে হেসে উঠেছিলাম, কিন্তু স্যার ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন৷ কারণ, ওই কার্নিশ থেকে অজয় যদি অসাবধানে পড়ে যায়!
এক অদ্ভুত স্নেহমাখা গলায় পীতাম্বরবাবু ডেকে উঠেছিলেন, ‘বাবা অজয়, আয় বাবা, ক্লাসের ভেতরে চলে আয়৷ অ্যাই, তোরা কয়েকজন ওকে হেলপ কর৷ সাবধানে ধরে ওকে ক্লাসের ভেতরে নামা…৷’
আমরা কয়েকজন অজয়কে হেলপ করার জন্যে উঠে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই অজয় জানলা দিয়ে ঢুকে এল, এক লাফে নেমে পড়ল ক্লাসরুমে৷
আমরা সবাই চুপ৷ মনে একটা কী হয়, কী হয় ভাব৷ লক্ষ করলাম, পীতাম্বরবাবু এবার পালটে গেছেন৷ একটু আগের আশঙ্কা, স্নেহ এখন উধাও৷ তার বদলে তিনি ঠান্ডা চোখে অজয়ের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন৷ এমন ঠান্ডা সেই দৃষ্টি যে, ওঁর চোখের পাতাও পড়ছে না৷
স্যার যেন হিসহিস করে অজয়কে কাছে ডাকলেন, ‘আয়, এদিকে আয়…৷’ তারপর ফার্স্ট বেঞ্চে স্যারের কাছাকাছি বসা অশোক নামের এক সহপাঠীকে বললেন, ‘অশোক, তোর স্কেলটা দে তো৷’
অশোক বরাবরই স্যারদের প্রতি অনুগত প্রাণ৷ ও সঙ্গে-সঙ্গে নিজের স্কেল বাড়িয়ে দিল স্যারের দিকে! সে-আমলের কাঠের স্কেল—এক ফুট লম্বা৷
পীতাম্বরবাবু অস্বাভাবিকরকম রেগে গেলে তবেই শারীরিক আক্রমণের পথে যেতেন৷ এবং সেইসব আক্রমণে ওঁর বরাবরের হাতিয়ার ছিল স্কেল৷
অজয় পায়ে-পায়ে স্যারের কাছে এগিয়ে গেল৷ ক্লাসরুম থমথম করছে৷ কারও মুখে কোনও কথা নেই৷
‘জানলার বাইরে ওই কার্নিশে গিয়ে উঠেছিলিস কেন?’ স্যার কথা বলার সঙ্গে-সঙ্গে বাতাসে স্কেল নাড়ছিলেন৷
‘কার্নিশে গিয়ে তো উঠিনি, স্যার৷ জানলার বাইরে ওই যে শিমুল গাছটা রয়েছে, ওটা বেয়ে পার্কে নেমে গিয়েছিলাম…৷’
এই পর্যন্ত শোনামাত্রই বাতাসে স্কেল নাড়ার ব্যাপারটা থেমে গেল৷ দেখলাম, স্যার গোল-গোল চোখ করে অজয়ের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন৷ অজয় তখনও ওর অ্যাডভেঞ্চারের কৈফিয়ত দিয়ে চলেছে৷
‘পার্কে স্যার, একটা কাঠগোলাপ গাছ আছে৷ তাতে অনেক ফুল৷ আর কী সুন্দর গন্ধ!’ এ-কথা বলার সঙ্গে-সঙ্গে পকেট থেকে রুমালের একটা পোঁটলা বের করে ফেলেছে অজয়৷ রুমালের ঢাকনা সরাতেই প্রকাশিত হল একরাশ কাঠগোলাপ ফুল৷ তাদের অসংখ্য সাদা পাপড়ি৷ আর অদ্ভুত সুন্দর গন্ধ৷
স্যারের দিকে ফুলের আঁজলা বাড়িয়ে অজয় বলল, ‘আপনি এগুলো নিন, স্যার—খুব সুন্দর ফুল…৷’
পীতাম্বরবাবু পলকে আবার পালটে গেলেন৷ অশোকের স্কেল টেবিলে রেখে অজয়ের হাত থেকে ফুলগুলো নিলেন৷ সেগুলো টেবিলে রেখে অজয়ের চুল ঘেঁটে দিয়ে বললেন, ‘এত সুন্দর প্রাইজ কেউ কখনও আমায় দেয়নি রে! কিন্তু তাই বলে এত বড় রিসক কেউ নেয়৷ যদি পড়ে-টড়ে যেতি! যা, ডেস্কে গিয়ে বোস…৷’
সেদিন থেকেই অজয়কে আমি মনে-মনে ‘হিরো’ বলে মেনে নিয়েছিলাম৷
অজয় ফুটবল খেলতে ভালোবাসত—আর সেটা খেলতও বেশ৷ ওর গাঁট্টাগোঁট্টা শরীরে বয়েসের তুলনায় শক্তি অনেকটাই বেশি ছিল৷ ফুল ব্যাক পজিশানে খেলে সেই শক্তি ও দিব্যি কাজে লাগাত৷
আমাদের স্কুলের ভেতরে সিমেন্ট বাঁধানো উঠোন ছিল৷ উঠোনটার চেহারা ছিল ইংরেজি ‘L’ অক্ষরের মতো৷ আমাদের টিফিনের জন্যে বরাদ্দ সময় ছিল মাত্র কুড়ি মিনিট৷ টিফিন খাওয়ার পর যেটুকু সময় হাতে থাকত সেই সময়টা আমরা অনেকেই একটা ইটের টুকরোকে ‘ফুটবল’ বানিয়ে সেই বাঁধানো উঠোনে দিব্যি ফুটবল খেলতাম৷ আমাদের পায়ে থাকত কালো রঙের চামড়ার বুটজুতো—যেটা স্কুল ড্রেসেরই অঙ্গ৷ ফলে ওই বিচিত্র ‘ফুটবল’ খেলার সময় পায়ে চোট পাওয়ার তেমন ভয় ছিল না৷
ওই ‘ফুটবল’ খেলার সময়েই আমি অজয়ের বাড়তি শক্তির ব্যাপারটা বেশ টের পেয়েছিলাম৷
অজয়কে নিয়ে দ্বিতীয় যে-ঘটনাটার কথা মনে পড়ছে সেটা হয়েছিল ইতিহাসের স্যার রমাপদবাবুর ক্লাসে৷
রমাপদবাবু ভীষণ রোগা ছিলেন৷ হাত-পাগুলো ছিল দড়ি পাকানো৷ নাকটা ঈগল পাখির মতো৷ গাল ভাঙা৷ সবসময়েই বিরক্তিতে যেন কপাল কুঁচকে আছেন৷
ওঁর চোখে চশমা ছিল৷ ধুতির খুঁট দিয়ে সেই চশমার কাচ পরিষ্কার করাটা ওঁর একরকম মুদ্রাদোষ ছিল বলা যায়৷
আমরা স্যারের ডাকনাম দিয়েছিলাম ‘কঞ্চি’৷ সেই নামটা আমরা শুধু নিজেদের মধ্যেই ব্যবহার করতাম৷
আর স্যার আমাদের সব্বাইকে একটাই নামে ডাকতেন: ‘বাঁদর৷’ শুধু মাঝে-মাঝে ওঁর পছন্দসই কোনও বিশেষণ ওই ‘বাঁদর’ শব্দটার আগে বসিয়ে দিতেন৷ যেমন, আমাদের চেহারার সাইজ দেখে রমাপদবাবু কাউকে বলতেন ‘বড় বাঁদর’, কাউকে বলতেন ‘মিডিয়াম বাঁদর’৷ আবার কাউকে বলতেন ‘ছোট বাঁদর’৷ তবে অজয়ের জন্যে স্যারের স্পেশাল ডাক ছিল ‘লঙ্কা বাঁদর’৷ এই নামের যে কী তাৎপর্য তা আমরা কখনও বুঝতে পারিনি৷
রমাপদবাবু সবসময় বলতেন, ‘শোন, প্রত্যেকটা মোমেন্টে আমাদের বয়েস বাড়ে৷ বয়েস বাড়ে, আর ইতিহাস তৈরি হয়—বুঝলি? এই যে চল্লিশ মিনিট ধরে তোরা আমার ক্লাস করলি, তোদের সবার বয়েস ফর্টি মিনিটস করে বেড়ে গেল, আর হিস্ট্রি তৈরি হয়ে গেল৷ ইতিহাস এত চুপিচুপি তৈরি হয় যে, খেয়াল না করলে টের পাওয়া যায় না৷’
এই ধরনের কথাবার্তা রমাপদবাবুর ফেভারিট ছিল৷ সুযোগ পেলেই সেগুলো একদফা করে আউড়ে নিতেন৷ সবসময়েই বোঝাতে চাইতেন যে, বিষয় হিসেবে ইতিহাস কী সাংঘাতিক গুরুত্বপূর্ণ৷
একদিন রমাপদবাবুর ক্লাস চলছিল৷ ক্লাসের মাঝামাঝি সময়ে ফোর্থ বেঞ্চ থেকে অজয় হাত তুলল: ‘স্যার, একটু বাইরে যাব?’
‘কেন রে, লঙ্কা বাঁদর? কী এমন জরুরি কাজ পড়ল যে বাইরে যাবি?’
উত্তরে অজয় ওর বাঁ-হাতের কড়ে আঙুলটা উঁচিয়ে দেখাল: ‘ছোট বাইরে যাব, স্যার—৷’ নরম সুরে অজয়ের আবেদন শোনা গেল৷
‘যা, যা—চটপট সেরে আয়৷’
স্যারের অনুমতি পাওয়ামাত্রই অজয় চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে এবং ক্লাসরুমের দরজার দিকে চটপটে পায়ে রওনা দিয়েছে৷
ব্যাপারটা সাদামাঠা ‘ছোট বাইরে’-র কেস বলেই আমরা সবাই ধরে নিয়েছিলাম৷ কিন্তু বহু মিনিট পেরিয়ে যাওয়ার পরেও অজয় ফিরছে না দেখে আমরা কেউ-কেউ প্রমাদ গুনলাম৷
সাধারণত ‘ছোট বাইরে’-র অপারেশানে বড়জোর তিন কি চার মিনিট লাগে৷ কিন্তু অজয় তো দেখছি প্রায় বিশ মিনিট পার করে দিয়েছে!
রমাপদবাবু পড়ানোর ফাঁকে-ফাঁকে বারবার দরজার দিকে তাকাচ্ছিলেন৷ দেখছিলেন, অজয় ফিরল কি না৷
হঠাৎ সবাইকে চমকে দিয়ে ক্লাসের দরজায় অজয় এসে হাজির৷
‘স্যার, আসব?’
স্যার অজয়ের দিকে তাকালেন৷ আমরাও৷
আমরা সবাই একসঙ্গে অবাক হয়ে গেলাম৷ কারণ, অজয়ের মাথা ভরতি পাকাচুল!
‘ক-কী-কী রে? তোর মাথার এ কী অবস্থা হয়েছে?’
অজয় বলল, ‘স্যার, আমার বয়েস বেড়ে গেছে৷’
আমরা সবাই হো-হো করে হেসে উঠলাম৷
স্যার আমাদের দিকে ফিরে ‘চোপ!’ বলে ধমক দিয়ে অজয়কে আবার জিগ্যেস করলেন, ‘বাথরুমে গিয়ে এতক্ষণ ধরে কী করছিলি, হতভাগা?’
‘চুপিচুপি ইতিহাস তৈরি করছিলাম, স্যার৷’ অজয়ের নিষ্পাপ উত্তর৷
এরপর যে-হাসির রোল উঠেছিল, স্যারের মালটিপল ধমকও তাকে থামাতে পারল না৷
উত্তেজিত রমাপদবাবু চেয়ার ছেড়ে তিরবেগে ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন অজয়ের ওপরে৷ ওর চুলের মুঠি ধরে গালে একটা থাপ্পড় কষালেন৷
হয়তো স্যার আরও কিছু করতেন, কিন্তু তার আগেই পিরিয়ড শেষের ঘণ্টা পড়ে গেল৷ এবং অজয়ও বেঁচে গেল৷
স্যার চলে যেতেই অজয়কে আমরা অনেকে চেপে ধরেছিলাম: ‘বল, কী করে তোর চুল পাকালি?’
অজয় হেসে বলল, ‘আটা দিয়ে৷ বাড়ি থেকে খানিকটা আটা ঠোঙায় করে নিয়ে এসেছিলাম৷ বাথরুমে গিয়ে সেই আটা মাথায় বুলিয়ে নিয়েছিলাম৷ দেশের বাড়িতে দেখেছি, যাত্রাপালায় মাথায় আটা বুলিয়ে মেকাপ নিচ্ছে, চুল পাকাচ্ছে—৷’
আমরা সবাই আলোচনা করতে লাগলাম, অজয় রমাপদবাবুকে রীতিমতো ‘ঐতিহাসিক’ ধাক্কা দিয়েছে৷
বন্ধুদের কার কাছে যেন শুনেছিলাম, অজয়দের একটা ছোট্ট মনিহারি দোকান আছে—কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের (এখন যার নাম বিধান সরণি) ট্রামরাস্তার ওপরে৷ নাম ‘দাদুভাই স্টোর্স’৷ অজয়ের বাবা দোকান চালান৷ আর অজয় নাকি স্কুল ছুটির পর সন্ধেবেলা দু-ঘণ্টা করে দোকানে বসে, বাবাকে একটু বিশ্রাম দেয়৷
আমি হাতিবাগান থেকে রোজ স্কুলে যাতায়াত করতাম—ওই কর্নওয়ালিস স্ট্রিট ধরে৷ যাতায়াতের পথে ট্রাম কিংবা বাস থেকে গলা বাড়িয়ে অজয়দের দোকানটাকে খুঁজতাম৷
দেখতে-দেখতে একদিন খুঁজেও পেলাম৷ ছোট্ট মলিন দোকান৷ রংচটা সাইনবোর্ড৷ দোকানে ধুতি আর ফতুয়া পরে একজন রোগামতন বয়স্ক মানুষ বসে আছেন৷ গাল বসা, মাথায় টাক৷ খোঁচা-খোঁচা কাঁচাপাকা দাড়ি-গোঁফ৷ অজয়ের বাবা৷
দোকানটাকে খুঁজে পাওয়ার পর থেকেই স্কুলে যাতায়াতের পথে আমার চোখ আমার অজান্তে ‘দাদুভাই স্টোর্স’-কে খুঁজে বেড়াত৷ এবং পেয়েও যেত৷
ক্লাস এইটে ওঠার পরেও অজয়ের সঙ্গে একই সেকশানে পড়ার ‘সৌভাগ্য’ আমার হয়েছিল৷ সেই ক্লাসে অজয় এমন এক কীর্তি ঘটিয়ে বসেছিল যেটা আমি আজও ভুলতে পারিনি৷
ব্যাপারটা হয়েছিল হরিনাথবাবুর ক্লাসে৷
এখানে হরিনাথবাবু সম্পর্কে দু-চারটে কথা বলা দরকার৷
তিনি আমাদের অ্যাডিশন্যাল ইংলিশ পড়াতেন৷ অর্থাৎ, প্রথাগত ইংরেজি ক্লাসে যে-টেক্সট বই বা গ্রামার পড়ানো হত, ওঁর পড়ানোর এলাকা ছিল তার বাইরে৷ ফলে হরিনাথবাবুর ক্লাসে আমরা নতুন-নতুন ইংরেজি শব্দ আর সেসব শব্দ দিয়ে মজার-মজার বাক্যরচনা, কিংবা শব্দের জাগলারি শিখতাম৷
যেমন, তিনি ক্লাসে প্রশ্ন ছুড়ে দিতেন, ‘বল—, How can you make a mile smile?’
আমরা উত্তর না দিয়ে স্যারের মুখের দিকে তাকিয়ে চুপচাপ বসে থাকতাম৷
পাঁচ কি দশ সেকেন্ড অপেক্ষা করার পর স্যার হেসে বলতেন, ‘এই সহজ প্রশ্নটার উত্তর কেউ দিতে পারলি না? The letter ”s” makes a mile smile, বুঝলি?’
হরিনাথবাবু মাঝবয়েসি মানুষ৷ চোখে গোল-গোল কাচের চশমা৷ মাথায় কদমছাঁট চুল৷ উচ্চতায় খুব খাটো ছিলেন৷ সবসময় ধুতি আর পাঞ্জাবি পরতেন৷ আর হাঁটতেন আরশোলার মতো তাড়াতাড়ি৷ স্কুলের লম্বা বারান্দা ধরে ওঁর হেঁটে যাওয়া দেখলে আমরা হাসি চেপে রাখতে পারতাম না৷ শুধুমাত্র হাঁটার ঢঙের জন্যেই আমরা স্যারের গোপন ডাকনাম রেখেছিলাম ‘ককরোচ’৷
হরিনাথবাবুর মধ্যে একটা কমিক-কমিক ব্যাপার ছিল৷ তা ছাড়া ওঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে আমাদের নিজেদের মধ্যে নানান তর্ক-বিতর্ক চলত৷ এর কারণ ছিল আমাদের বাৎসরিক স্কুল ম্যাগাজিন৷
আমাদের স্কুল ম্যাগাজিনে হেডস্যার থেকে শুরু করে সব টিচারের নাম ছাপা হত৷ আর সেই নামের পাশে-পাশে ছাপা হত স্যারদের সব অ্যাকাডেমিক ডিগ্রি৷ সেই ম্যাগাজিনেই আমরা দেখেছিলাম, আমাদের অঙ্ক স্যারের এম. এ. ডিগ্রি—যা বহুকাল হল দেখা যায় না৷ আমাদের বাংলা স্যার পীতাম্বরবাবুর নামের পাশে ডবল এম. এ. ডিগ্রি ছিল—একটা বাংলায়, আর অন্যটা সংস্কৃতে৷ সেই ডবল এম. এ. ডিগ্রিও অনেক বছর হল উধাও৷
তো নানান স্যারের নানান ডিগ্রির মধ্যে হরিনাথবাবুর নামটা আমাদের চোখে কটকট করত, কারণ স্যারের নামের পাশে কোনও ডিগ্রিই লেখা থাকত না৷ ব্যাপারটা আমাদের ভারী অদ্ভুত লাগত৷ তাই স্যার আসলে যে ঠিক কী পাশ, কতটুকু পাশ, এসব নিয়ে আমরা আলোচনা করতাম৷ এসব আলোচনা যে অশোভন এবং অন্যায় সেটা ওই ছোট বয়েসে আমরা বুঝতে পারিনি৷ তবে স্কুল কর্তৃপক্ষও স্কুল ম্যাগাজিনে স্যারদের নামের পাশে-পাশে তাঁদের অ্যাকাডেমিক ডিগ্রি ছাপার প্রথাটা না রাখলেই পারতেন৷ ছাত্রদের কাছে স্যারদের শুধু নামই কি যথেষ্ট নয়!
সে যা-ই হোক, হরিনাথবাবু একদিন অজয়ের দুষ্টুমির শিকার হলেন৷
স্যার ক্লাসে হাসি-হাসি মুখ করে আমাদের ইংরেজি শেখাচ্ছিলেন—অ্যাডিশনাল ইংলিশ৷ যেটাকে আমরা কখনও-কখনও বলতাম ‘বাড়তি’ ইংরেজি৷
যেমন, স্যার প্রশ্ন করতেন, How a lot goes through a slot?
আমরা উত্তর দিতে পারি বা না পারি, স্যার একটু পরেই হেসে বলতেন, ‘The letter ”s” makes a lot go through a slot,’—বুঝলি?’
এরকমই আর-একটা প্রশ্ন ছিল, ‘What makes a road broad?’
এভাবেই আমরা হরিনাথবাবুর কাছে ‘বাড়তি’ ইংরেজি শিখতাম৷
একদিন ক্লাস চলার সময় অজয় হাত তুলে স্যারের কাছে বাথরুমে যাওয়ার পারমিশান চাইল৷
কোনও স্যারের ক্লাসের মাঝে অজয় বাথরুমে যাওয়ার পারমিশান চাইলেই আমরা নতুন কোনও দুষ্টুমি দেখার প্রত্যাশায় থাকতাম৷
হরিনাথবাবু অজয়কে জিগ্যেস করলেন, ‘বিগ অর স্মল?’
অজয় বলল, ‘লিকুইড, স্যার—৷’
অজয়ের মুখে ‘লিকুইড’ শুনে আমরা সবাই তো হেসে খুন৷ কিন্তু হরিনাথবাবু কী এক আশ্চর্য ক্ষমতায় নিজের গাম্ভীর্য ধরে রাখলেন৷ তিনি তাড়াতাড়ি অজয়কে অনুমতি দিয়ে ব্যাপারটার নিষ্পত্তি করলেন৷
‘যা, তবে তাড়াতাড়ি ফিরে আসবি—৷’
অজয় মুখে কোনও কথা না বলে প্রায় চল্লিশ ডিগ্রি ঘাড় হেলিয়ে দিল এবং চটপট পা চালিয়ে ক্লাস থেকে বেরিয়ে গেল৷
কিন্তু ও ফিরে এল এক মিনিটের মধ্যেই৷
‘মে আই কাম ইন, স্যার?’
গলাটা অজয়ের, কিন্তু মানুষটা কে?
মোটা লোমশ ভুরু৷ চোখে এক অদ্ভুত চশমা৷ চশমার দুটো সার্কেলের মাঝে বিশাল মাপের খাড়া গোলাপি নাক৷ সেই নাকের নীচে পাকানো মোচ৷
কে এই লোকটা?
আসলে ব্যাপারটা হল, সেই সময়ে প্লাস্টিকের এই খেলনাটা কিনতে পাওয়া যেত৷ ভুরু, চশমা, নাক এবং ওই পেল্লায় মোচ একইসঙ্গে আটকানো—অনেকটা একটা মুখোশের মতো৷ তবে সেই চশমায় কাচ অথবা প্লাস্টিকের কোনও লেন্স থাকত না৷
বাথরুমে যাওয়ার নাম করে অজয় বাইরে গিয়ে নিজের চশমাটা পকেটে পুরে তার বদলে ভুরু-চশমা-নাক-মোচের এই অদ্ভুত মুখোশটি পরে নিয়েছে৷ তারপর কেউকেটা এক অচেনা আগন্তুক সেজে হরিনাথ স্যারের ক্লাসে ফিরে এসেছে৷
হরিনাথবাবু একটা তীক্ষ্ণ চিৎকার করে অজয়কে লক্ষ্য করে লাফ দিলেন৷ এবং দরজার প্রায় কাছাকাছি গিয়ে ল্যান্ড করলেন৷ একইসঙ্গে স্যারের মুখ দিয়ে দুটো গালাগাল বেরিয়ে এল৷ প্রথম গালাগালটা খুবই সাধারণ মানের৷ একটি মাত্র শব্দে তৈরি৷ দু-অক্ষরের শব্দ—যার শেষ অক্ষরটি ‘লা’৷
আর দ্বিতীয় গালাগালটি কিঞ্চিৎ উন্নত মানের৷ দুটি শব্দে তৈরি—যার সাহায্যে কোনও ব্যক্তিকে একটি বিশেষ পশুর সন্তান হিসেবে সম্বোধন করা হয়৷
হরিনাথ স্যারের মুখে আচমকা এইরকম একজোড়া অশিষ্ট সম্বোধন শুনে আমরা যেমন আঁতকে উঠেছি, তেমনই—অন্যায়ভাবে—অদ্ভুত একটু মজাও পেয়েছি৷
কিন্তু স্যার ওকে ধরে ফেলার আগেই অজয় দে ছুট৷ আর কী আশ্চর্য, স্যারও ওকে তাড়া করলেন!
ক্লাসরুমের করিডরের দিকের জানলা দিয়ে আমরা কেউ-কেউ বডি অর্ধেক ঝুঁকিয়ে দিয়ে সেই রেস দেখতে লাগলাম৷ আর বাকিরা ভিড় জমাল ক্লাসরুমের দরজায়৷
সে এক অদ্ভুত দৃশ্য!
স্কুলের লম্বা-চওড়া করিডর ধরে অজয় তিরবেগে দৌড়চ্ছে৷ আর ওর বেশ খানিকটা পেছনে ছুটে চলেছে ‘ককরোচ’ স্যার৷
একটা ভারী খাতা হাতে উলটোদিক থেকে হেঁটে আসছিল তৃপ্তিদা—আমাদের স্কুলের পিওন৷ তৃপ্তিদা একটু দুলে-দুলে হাঁটত৷ তাই আমরা ওর নাম দিয়েছিলাম ‘দোলনা’৷
স্যার বোধহয় ছুটে-ছুটে হাঁপিয়ে পড়েছিলেন৷ তাই তৃপ্তিদাকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়লেন৷ অজয়ের দিকে আঙুল দেখিয়ে চিৎকার করে বললেন, ‘অ্যাই তৃপ্তি,কে এক্ষুনি হেডস্যারের কাছে নিয়ে যা—৷’
চার অক্ষরের এই তৃতীয় গালাগালটি দ্বিতীয়টির তুলনায় আরও কিছুটা উন্নত মানের৷ এবং একইসঙ্গে বেশ ধাক্কা দেওয়ার মতো৷ আমরা তো সে-ধাক্কা খেয়েই ছিলাম, দেখলাম তৃপ্তিদাও ধাক্কা খেয়ে করিডরে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে৷
না, অজয়কে ধরা যায়নি৷ ও ততক্ষণে পগার পার৷ হয়তো ছুটে পালিয়ে গিয়ে বারান্দার পাশের কোনও গাছ বেয়ে নীচের উঠোনে নেমে গেছে৷
এই ঘটনার দু-চারদিন পর থেকে হরিনাথ স্যারকে স্কুলে আর দেখিনি৷ কানাঘুষোয় শুনেছিলাম, স্কুলের মধ্যে অশিষ্ট শব্দ ব্যবহারের জন্যে ওঁকে স্কুল ছাড়তে হয়েছে৷
এ-ঘটনায় অজয়েরও মনখারাপ হয়ে গিয়েছিল৷ কারণ, ও স্যারের সঙ্গে নিছকই একটু মজা করতে চেয়েছিল৷ তার ফল যে এমনটা হবে সেটা ও ভাবতে পারেনি৷
ক্লাস এইটের পর অজয়ের সঙ্গে আর পড়ার সুযোগ পাইনি৷ কারণ, ক্লাস নাইন থেকে ছাত্রদের চারটি শাখায় ভাগ করা হত—সায়েন্স, টেকনিক্যাল, আর্টস ও কমার্স৷ আমি সায়েন্স নিয়ে পড়েছিলাম, অজয় নিশ্চয়ই অন্য কোনও শাখায় পড়াশোনা করেছিল৷ ফলে আমার সঙ্গে ওর দেখা হয়নি৷
কথাটা ভুল বলা হল৷ আমার বলা উচিত, আমি ওকে দেখতে পাইনি৷ কারণ, অজয় আমাদের কাউকেই সেভাবে চিনত না, কিন্তু আমরা সব্বাই ওকে চিনতাম৷ আর আমি বোধহয় মনে-মনে একটু-একটু অজয় হতে চাইতাম৷
স্কুলের পালা শেষ হল আমার৷ হয়তো অজয়েরও৷ তারপর সময়ের স্রোতে পেরিয়ে গেল প্রায় পঞ্চাশ বছর৷ আমি অজয়কে ভুলিনি৷ ভুলিনি ‘দাদুভাই স্টোর্স’ দোকানটিকেও৷ কিন্তু কাজের জগৎ আমাকে কলকাতার অন্যান্য অঞ্চলে এমন ব্যস্ত করে তুলল যে, ‘দাদুভাই স্টোর্স’-এর রাস্তায় কখনও যাওয়া হয়নি৷ যদি বা কখনও গিয়ে থাকি, আমার মন তখন এতই ব্যস্ত ছিল যে, দোকানটা খেয়াল করিনি৷
কিন্তু গতকাল সন্ধেবেলা একটা ব্যাপার হল৷ বাড়ির একটা জরুরি কাজে একজন ল’ইয়ারের চেম্বারে গিয়েছিলাম৷ কথাবার্তা শেষ করে বিধান সরণির ট্রামরাস্তার ধারে বাস ধরব বলে দাঁড়িয়ে আছি, হঠাৎই চোখ গেল উলটোদিকের ফুটপাথের একটা ছোট্ট দোকানের দিকে৷ জীর্ণ, মলিন চেহারা৷ তোবড়ানো সাইনবোর্ড৷ দোকানের নামের কয়েকটা অক্ষর মুছে গেলেও ‘ভাই’ এবং ‘স্টো’ অংশ দুটো পড়া যাচ্ছে৷ অজয়দের দোকান!
আমার পা দুটো সঙ্গে-সঙ্গে রাস্তা পার হয়ে গেল৷ আমার দ্বিধা-সঙ্কোচকে পাত্তা না দিয়ে ওরা সটান গিয়ে হাজির হয়ে গেল অজয়ের দোকানের সামনে৷
কিন্তু কোথায় অজয়?
দোকানে বসে আছে আঠেরো-উনিশ বছরের একটি ছেলে৷ রোগা৷ মাজা রং৷ সবে দাড়ি-গোঁফ উঠেছে৷ চোখ দুটো বড়-বড়—যাকে পরিভাষায় আয়ত বলে৷ মাথার চুল খাড়া-খাড়া৷ গায়ে একটা চেক-চেক হাওয়াই শার্ট৷ পায়ে পাজামা৷
দোকানের শো-কেস ময়লা৷ কাচ দু-তিন জায়গায় ফাটা৷ সেইসব ফাটল পিভিসি টেপ দিয়ে তাপ্পি মারা৷
দোকানের শো-কেসের ভেতরে হরেকরকম বলপয়েন্ট পেন, পেনসিল আর রিফিল৷ দু-পাশের তাকে লাট করে রাখা খাতা আর দিস্তে কাগজ৷ দোকানের ডানদিকে সুতোয় বাঁধা অনেকগুলো প্লাস্টিকের বল আর খেলনাপাতি ঝুলছে৷ বোঝাই যাচ্ছে, খাতা, পেন, পেনসিলের পাশাপাশি বাচ্চাদের টুকিটাকি খেলনাও ‘দাদুভাই স্টোর্স’ বিক্রি করে থাকে৷
বাঁ-দিকের তাকগুলোর মাঝে একটা ছোট্ট খাঁজে ঠাকুরের আসন চোখে পড়ল৷ সেখানে খুব সরু-সরু কালো রঙের ধূপকাঠি জ্বলছে৷
দোকানে দাঁড়ানো ছেলেটিকে ভালো করে দেখলাম৷
না, আমার স্মৃতিতে অমলিন অজয়ের মুখের আদলের সঙ্গে ছেলেটির মুখের আদল কিছুতেই মিলছে না৷
তা হলে কি অজয়দের দোকানটার হাতবদল হয়েছে? পঞ্চাশ বছর সময়ের মধ্যে সেটা হতেই পারে৷ একবার কেন, দু-চারবারও হাতবদল হয়ে থাকতে পারে৷ কিন্তু ছেলেটিকে অজয়ের কথা একটিবার অন্তত জিগ্যেস না করে আমি ফিরে যাব না৷
‘ভাই, এটা কি অজয়দের দোকান? অজয়—মানে, আমার সঙ্গে ও স্কুলে পড়ত…৷’
ছেলেটি হেসে বলল, ‘আপনি আমার বাবাকে চেনেন? হ্যাঁ, বাবা ওই স্কুলটাতেই পড়ত—৷’
‘অনেক বছর পর ওর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি—একবার দেখা করা যাবে?’
ছেলেটি ঘাড় কাত করল: ‘হ্যাঁ—কেন যাবে না? বাবা তো সবসময় বাড়িতেই থাকে…৷’
কথা বলতে-বলতে ছেলেটি কাউন্টারের কাঠের ডালা তুলে দোকানের বাইরে বেরিয়ে এল৷ হাত দুটো ঘষে-ঘষে পাজামায় মুছল৷ পাশেই একটা ছোট টেলারিং-এর দোকান ছিল৷ সেই দোকানের ভেতরে গলা বাড়িয়ে ছেলেটি কাকে যেন বলল, ‘পারভেজদা, আমার দোকানটা একটু দেখো তো৷ আমি এই কাকুকে একটু বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসছি৷ উনি বাবার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন—৷’
টেলারিং-এর দোকানের ভেতর থেকে কারও তীক্ষ্ণ গলা শোনা গেল: ‘ঠিক আছে৷ তবে জলদি-জলদি ব্যাক কোরো—৷’
আমরা রওনা হলাম৷ ছেলেটি আগে, আমি পেছনে৷
বড় রাস্তা ছেড়ে বাঁ-দিকের গলি৷ সেই গলিতে কিছুটা হেঁটে যাওয়ার পরই আবার বাঁ-দিক৷ এবারে আরও সরু একটা গলি৷ সেখানে অনেক পুরোনো-পুরোনো খাটো মাপের সব বাড়ি৷ তারপর কয়েকটা বাড়ির পরেই একটা মলিন বাড়ির ছোট্ট দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ল ছেলেটা৷ পেছন ফিরে আমাকে ডাকল, ‘আসুন—৷’
শেষ পর্যন্ত একটা ঘরে এসে পৌঁছোলাম৷
ছোট মাপের ঘর৷ বাতাসে পুরোনো গন্ধ৷ ঘরে একটা খাট, আর দুটো টুল৷ একপাশে একটা টেবিলে বই, খবরের কাগজ আর কয়েকটা জামাকাপড় ডাঁই করা৷ দেওয়ালের কোণে একটা সেলাই-মেশিন৷ দেখেই বোঝা যায়, বহুদিন ওই মেশিনে কেউ হাত দেয়নি৷
ঘরের শেষ আইটেম হল, বিছানায় বসে থাকা একজন বয়স্ক মানুষ৷ খালি গা, পরনে লুঙ্গি, রোগা, গাল বসা, মাথায় টাক৷ খোঁচা-খোঁচা কাঁচাপাকা দাড়ি- গোঁফ৷ পাঁচ দশক আগে দূর থেকে যে-মানুষটিকে আমি ‘দাদুভাই স্টোর্স’-এর কাউন্টারে দেখেছিলাম৷
তখনই আমি অজয়কে চিনতে পারলাম৷
ছেলেটি আমাকে দেখিয়ে বলল, ‘বাবা, ইনি তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন—তোমার স্কুলের বন্ধু…৷’
অজয় আমাকে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল৷ বোধহয় পুরোনো ‘আমি’-টাকে খুঁজছিল৷
একটা টুল দেখিয়ে ছেলেটি আমাকে বলল, ‘আপনি বসুন৷ বাবার সঙ্গে কথা বলুন৷ আমি দোকানে যাই—নইলে পারভেজদা আবার খচে যাবে—৷’
এই কথা বলে অজয়ের ছেলে চলে গেল৷
আমি একটা টুল টেনে নিয়ে অজয়ের কাছে বসলাম৷
‘অজয়, কেমন আছ? আমি অনীশ—৷’
অল্প হেসে অজয় বলল, ‘ও—৷’
বুঝলাম, আমাকে ওর একটুও মনে নেই৷ আবার জিগ্যেস করলাম, ‘কেমন আছ তুমি?’
‘চলে যাচ্ছে, ভাই৷ গ্যাসট্রিকের পেইন নিয়ে আছি৷ লাস্ট মাসে হার্নিয়া অপারেশন হয়েছে৷’
মনে হচ্ছিল, আমার চেনা অজয় নয়, তার ছায়ার সঙ্গে আমি কথা বলছি৷
এরপর আমিই কথা বলতে লাগলাম৷ অজয় শুধু ‘হুঁ’, ‘হাঁ’ শব্দ করে ঠেকা দিতে লাগল৷
আমি ওর ছোটবেলার কাহিনি ওকেই শোনাতে লাগলাম৷ সেসব শুনে ও প্রথম-প্রথম ঠোঁটে হাসছিল, অল্প-অল্প মাথা নাড়ছিল৷ কিন্তু একটু পরেই কেমন যেন চুপ মেরে গেল৷
আমি কথা বলতে-বলতে সেই পুরোনো ‘অজয়’কে খুঁজছিলাম৷ কোথায় হারিয়ে গেল আমার সেদিনের সেই হিরো?
সেই ‘হিরো’-কে অজয়ও বোধহয় খুঁজছিল৷
হঠাৎই দেখলাম, ও ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল৷ মাথাটা ঝুঁকিয়ে দিল বুকের কাছে৷ ওর পলকা শরীরটা ফুলে-ফুলে উঠতে লাগল৷
আমারও কেমন একটা কষ্ট হচ্ছিল, তাই টুল ছেড়ে উঠে পড়লাম৷ চুপচাপ বেরিয়ে এলাম ওর ঘর থেকে৷
বুঝতে পারছিলাম, আজকের ‘অজয়’ সেদিনের সেই ‘অজয়’কে সবসময় খুঁজে চলেছে৷ খুব মিস করছে সেই দুষ্টু ছেলেটাকে৷
আসলে আমাদের প্রত্যেকের ভেতরে দুজন করে মানুষ থাকে৷ তারা বিশাল সময়ের দূরত্বে দাঁড়িয়েও হাতধরাধরি করে চলতে চায়৷ একে অপরকে মিস করে৷
কিন্তু ‘অজয়’-কে তো আমরা হারাতে চাই না!
আমি চাই, আমরা যারা-যারা ‘অজয়’ হতে পারিনি তাদের আকাঙ্ক্ষার মধ্যে ‘অজয়’-রা চিরকাল বেঁচে থাকুক৷