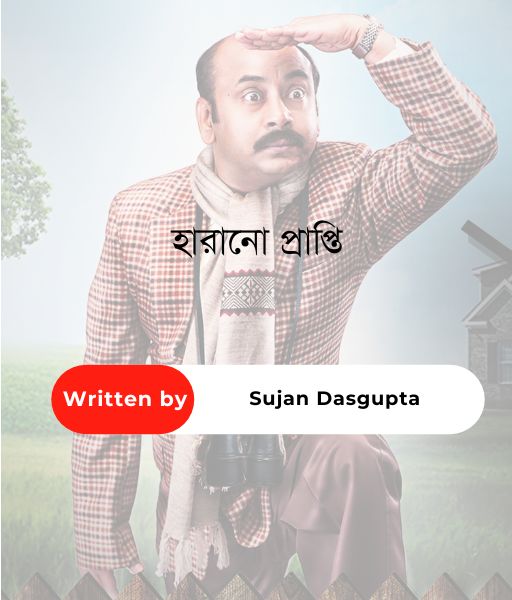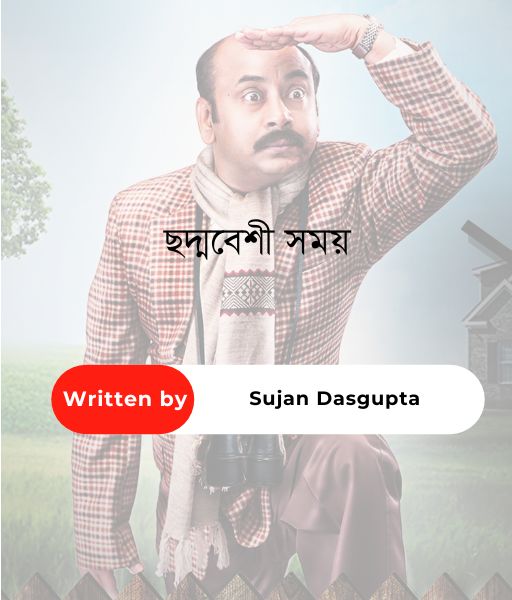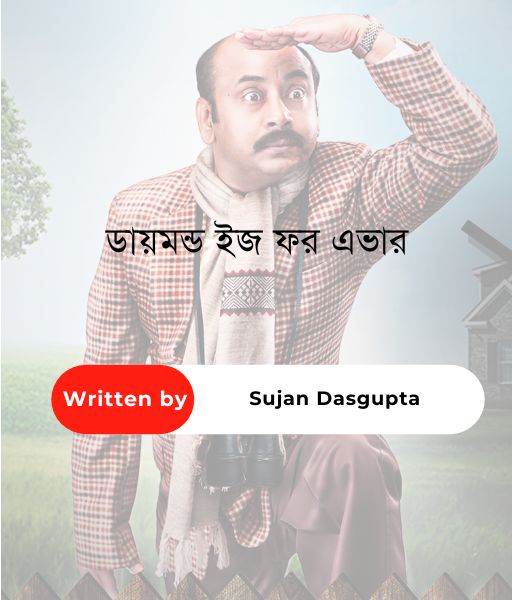আঙুলের ছাপ : 03
ডঃ রায়ের বাড়িটা সত্যিই ইম্প্রেসিভ! ঢুকতে হয় অবশ্য সরু রাস্তা দিয়ে, যেটা একসময় হয়তো পিচের ছিল, কিন্তু বীরভূমের ধুলোয় বোঝার উপায় নেই। রাস্তার দু-ধারে সারি সারি মাটির বাড়ি— মুরগি–ছাগলের রাজত্ব। একটু বাদে অবশ্য রাস্তার দু-ধার ফাঁকা হয়ে গেল। এদিক-ওদিক দু-একটা পাকা বাড়ির সামনে ফুলের বাগান। আরও একটু গেলে রাস্তা শেষ হয়েছে উঁচু পাঁচিল ঘেরা একটা বাড়ির সামনে। গেটের বাইরে পুলিশ, কৌতূহলী জনতাকে ধমকে তাড়াচ্ছে।
“এটাই ডঃ রায়ের বাড়ি ‘শান্তিকুঞ্জ”।”
গেটে দাঁড়ানো পুলিশদের সঙ্গে কয়েকটা কথা বলে দীপকবাবু আমাদের নিয়ে বাড়িতে ঢুকলেন। বারান্দায় উঠে বাইরের দরজা দিয়ে ঢুকলেই একটা চওড়া প্যাসেজ। তার বাঁ-দিকে দোতলায় যাবার কাঠের সিঁড়ি, আর ডান দিকে প্রথমেই মস্ত বড়ো ডবল ডোর। পাল্লা দুটো খোলা বলে বেশ কয়েকটা পেন্টিং ভেতরের দেয়ালে ঝুলছে দেখা যাচ্ছে।
প্যাসেজটা শেষ হয়েছে একটা বন্ধ দরজার সামনে। শেষ হবার মুখে ডান দিকে একটা ওয়াশরুম।
ওপরের তলায় উঠে প্রথমেই একটা হলের মতো জায়গা। হলের মুখোমুখি একটা ডবল ডোর, কিন্তু দুটো পাল্লাই বন্ধ। ডান দিকে হলটা শেষ হয়েছে বাড়ির সামনের ঢাকা বারান্দায়। সেখানে সাজানো কয়েকটা বেতের চেয়ার আর টেবিল। হলের অন্যদিকে গেলে প্রথমে বাঁ-দিকে কমন ওয়াশরুম, তারপর ছোট্ট একটা ঘর। ডান দিকে মাস্টার বেডরুম, ওখানেই ডঃ রায়ের বড়ি বিছানায় পড়েছিল। এদিকেও হলটা শেষ হয়েছে আর একটা ঢাকা বারান্দায়। সেখানে খাবার টেবিল আর চারটে চেয়ার সাজানো।
মাস্টার বেডরুমে ঢুকতেই চোখে পড়ল বিশাল খাট। পাশে নাইট স্ট্যান্ডে রিডিং ল্যাম্পের সামনে কয়েকটা বই। আয়না লাগানো বিল্ট-ইন ড্রেসার-কাম- ওয়ারড্রোব। কোণে একটা ইলেকট্রিক হিটার। প্লাগটা দেয়ালে আটকানো, কিন্তু সুইচটা অফ। তার পাশেই নিভিয়ে দেওয়া কেরোসিনের স্পেস হিটারটা।
“এটা থেকেই কার্বন মনোক্সাইড বেরোচ্ছিল।” দীপকবাবু বললেন।
“ঘরে ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাওয়া গেছে?”
“না, সুইচ বা কেরোসিন হিটারে মেলেনি। মনে হয় খুনির হাতে গ্লাভস ছিল।”
“জানলাগুলো কি বন্ধ করে শুতেন ডঃ রায়?”
“হ্যাঁ, দরজা-জানলা বন্ধ করেই শুতেন। দুপুরেও যখন ঘুমোতেন দরজা বন্ধ থাকত। সকালে নিতাই যখন আসে তখনও দরজা ভেজানো ছিল। ডাকাডাকিতে
সাড়া না পেয়ে ঘরে ঢোকে।”
“ধরে নিচ্ছি দরজাতেও কোনো ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাওয়া যায়নি।”
“শুধু নিতাই আর ডঃ রায়ের ফিঙ্গারপ্রিন্ট।”
জানলায় কোনো গ্রিল নেই। একেনবাবু জানলায় ঝুঁকে নীচের দিকে তাকালেন। একদিকে একটা কুয়ো, অন্যদিকে সবজি বাগান।
দীপকবাবুও পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন। বললেন, “কুয়োর জল মালি ব্যবহার করে গাছে জল দেবার জন্য। বাড়ির ব্যবহারের জন্য ডিপ টিউব-ওয়েল রয়েছে।”
বেডরুমে আর কিছু চোখে পড়ল না। সেখান থেকে বেরিয়ে সামনের বারান্দার কাছে বন্ধ ডবল ডোরের সামনে দাঁড়িয়ে একেনবাবু জিজ্ঞেস করলেন, “এখানে কী আছে?”
“ইউরোপিয়ান আর্টিস্টদের আঁকা কিছু ছবি। এয়ার কন্ডিশনার চলে বলে দুটো পাল্লাই বন্ধ থাকে।”
“আর নীচে যে ছবিগুলো দেখেছিলাম?” আমি জানতে চাইলাম।
“ওগুলো ইন্ডিয়ান আর্টিস্টদের আঁকা।”
“আর একটা প্রশ্ন, রান্নাঘর দেখছি না তো? ওটা কি এক তলায়?”
“রান্নাঘরটা বাড়ি থেকে একটু আলাদা। ডঃ রায় দুশ্চিন্তা করতেন তেলের ধোঁয়ায় ছবি যদি নষ্ট হয়ে যায়, বিশেষ করে ইউরোপের ছবিগুলো।”
আমরা ওপরের বারান্দায় কথাবার্তা বলতে একটু বসতেই নিতাই এল। “স্যারেরা চা খাবেন?”
নিতাইয়ের চোখের কোণে কালি। রাতে মনে হয় ঘুম হয়নি। সাহেবের মৃত্যুতে খুবই বিধ্বস্ত। চোখে-মুখে ভয়ের ছাপ, আর সেইসঙ্গে ভবিষ্যতের ভাবনা তো আছেই। “চা লাগবে না, নিতাই। তোমার সাহেবের মৃত্যু নিয়ে এঁরা তদন্ত করতে এসেছেন। তুমি বরং এঁদের প্রশ্নের ঠিকঠাক উত্তর দাও।”
নিতাই সন্ত্রস্তভাবে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। মাথা নীচু করে বলল, “বলুন, বাবু।”
একেনবাবু জিজ্ঞেস করলেন, “তুমি ক’দিন এ বাড়িতে কাজ করছ?”
“যেদিন থেকে সাহেব এ বাড়িতে এলেন।”
“সাহেবকে আগে চিনতে?”
“না, বাবু। কাজ খুঁজছি জেনে রঞ্জনবাবু ডেকে ললেন, ওঁর মামা আসছেন, লোকের দরকার। আমি কাজ করব কিনা। সেই থেকেই এখানে আছি।”
“রঞ্জনবাবুকে চিনতে?”
“হ্যাঁ, বাবু। আমার দিদি ওঁর বাড়িতে কাজ করে।”
“কেরোসিন হিটারটা কোত্থেকে এসেছিল জানো?”
“না, বাবু।”
“আগে দেখোনি?”
“দেখেছি, কয়েক দিন ধরেই আছে।”
“সাহেবকে জিজ্ঞেস করোনি, ওটা কেন ওখানে রয়েছে?”
“না।”
এই উত্তরে অবশ্য আশ্চর্য হলাম না। আমাদের দেশে কাজের লোকরা মনিবদের বেশি প্রশ্ন করতে সাহস পায় না।
আমাদের কথার মাঝখানেই একজন গার্ড এসে খবর দিল ডঃ রায়ের ভাইপো অজিতবাবু গেটে দাঁড়িয়ে আছেন।
“দোতলায় আসতে বলো।”
খানিক বাদেই এক দীর্ঘদেহী সুপুরুষ ওপরে উঠে এলেন।
“আসুন, অজিতবাবু, এঁদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই,” বলে দীপকবাবু আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন।
“আপনারাই কি কলকাতা থেকে এসেছেন কাকার মৃত্যুর ব্যাপারে?”
“হ্যাঁ স্যার, ভালোই হল আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আমাদের দুয়েকটা প্রশ্ন ছিল, সেগুলো এখনই করে ফেলতে পারি। আপনার অসুবিধা নেই তো স্যার?”
“না, না, অসুবিধার কী আছে! বলুন।”
“তুমি যেতে পারো,” বলে নিতাইকে বিদায় দিয়ে, অজিতবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন একেনবাবু, “আপনি তো স্যার ডঃ রায়ের খুবই কাছের লোক ছিলেন, তাই না?”
“হ্যাঁ, উনি আমার আপন কাকা ছিলেন।”
“আপনার কাকা যে একটা উইল করেছিলেন, খবরটা কি আপনি জানতেন?”
“আগে জানতাম না। কিন্তু কয়েক দিন আগে সিদ্ধার্থকাকা একটা আভাস দিয়েছিলেন।”
“সিদ্ধার্থকাকা?”
“কাকার ছেলেবেলার বন্ধু, একসময়ে এখানে পড়াতেন।”
“ও হ্যাঁ স্যার, ওঁর নাম শুনেছি। তা কী বলেছিলেন উনি?”
“কাকার উইলে আমার জন্য কিছু রাখা আছে, তবে বেশিরভাগই রঞ্জনের নামে।”
“আপনি অবাক হননি তাতে?”
“একটু অবাক নিশ্চয় হয়েছিলাম। তবে নিজের টাকা কাকা যাকে খুশি দেবেন, আমার কী বলার আছে! শুধু ছবিগুলো আমাকে দিয়ে গেলে সেগুলোকে যত্ন করে রাখতে পারতাম।”
“ছবিগুলো স্যার আপনাকে দিয়ে যাননি?”
“জানি না। যতটুকু জানি সেটাই বললাম। দিয়ে গেলে তো ভালোই। তবে কাকা বেঁচে থাকলেই সবচেয়ে ভালো হত।”
“আচ্ছা স্যার, ছবিগুলোর যত্ন করার ব্যাপারটা কী?”
“এখানকার ক্লাইমেট আগের মতো আর ড্রাই নেই, বেশ হিউমিড। ধুলোবালিও প্রচুর। অয়েল পেন্টিং সাধারণত কাচে ঢাকা থাকে না। তাই খুব নিয়মিত ফাইন ব্রাশ দিয়ে ধুলো ঝাড়তে হয়।”
“সেটা তো স্যার অনেক কাজ, বীরভূমের ধুলো বলে কথা! কাচে ঢেকে রাখলেই তো ঝামেলা চুকে যায়।”
“ঠিকই বলেছেন। এমনিতে অয়েল পেন্টিং-এ বার্নিশের কোটিং দেওয়া থাকে ময়েচার আর আলট্রা ভায়োলেট রে থেকে রক্ষা করার জন্য। সমস্যা ধুলো নিয়ে। তবে আলো-বাতাসে সব ছবিই ঔজ্জ্বল্য হারায়। কাকাকে যখন বলেছিলাম ছবিগুলো নতুন করে বাঁধানোর কথা, প্রথমে রাজি হননি। পরে যখন বুঝলেন আমিই কাজটা করে দেব, তখন মত দেন।”
“ফ্রেমিং করার কাজ স্যার আপনি জানেন?”
“হ্যাঁ, আমার একটা কোম্পানি আছে। খুব ভালো করে ফ্রেমিং না করলে কাচে-ঢাকা ফ্রেমের মধ্যেও ময়েস্চার জমে। এদেশে অনেকেই কাজটা ভালো জানে না। …দেখবেন আমার ফ্রেম-করা ছবিগুলো?”
“নিশ্চয় স্যার।”
অজিতবাবু নীচে সেই ডবল ডোর দেওয়া ঘরে আমাদের নিয়ে গেলেন। দেয়ালে বেশ কয়েকটি ঝকঝকে নতুন ফ্রেম-বন্দি ছবি। তবে চার দেয়ালের বেশিরভাগ জায়গাই ফাঁকা। আগে সেখানে ছবি ছিল বোঝা যায়।
“অনেকগুলো ছবি নতুন করে ফ্রেমে লাগানো হয়ে গেছে, এখনও ঝোলানো হয়নি।”
এটা শুনে চোখে পড়ল একটা চৌকিতে মোটা কাপড় দিয়ে কিছু ঢাকা। চৌকির পাশে ব্রাউন পেপারে প্যাক করা চারটে ছবি দেয়ালে হেলান দিয়ে রাখা। সেদিকে তাকাচ্ছি দেখে অজিতবাবু বললেন, “এদিকের দুটো প্যাক করে রেখেছি ফ্রেম করাতে নিয়ে যাব বলে। অন্য দুটো হয়ে গেছে।” কথাটা বলে ফিনি ছবি দুটো যখন মোটা কাপড়ের নীচে রাখতে যাচ্ছেন আমি সাহায্য করার জন্য তাতে হাত দিতেই উনি একেবারে হাঁ হাঁ করে উঠলেন।
“প্লিজ, ছবিগুলোতে হাত দেবেন না!
“সরি,” বলে তাড়াতাড়ি হাত সরিয়ে নিলাম। মনে হল ছবিগুলোর ব্যাপারে উনি ওভার-প্রোটেক্টিভ!
“কিছু মনে করবেন না, এই দুটো আমার প্রাণ–হুসেন আর অমৃতা শেরগিল। আমিই খুঁজে খুঁজে কাকাকে দিয়ে কিনিয়েছি। লোকাল আর্টিস্ট ছাড়াও কাকার এই কালেকশনে সোমনাথ হোড়, ধীরেন দেববর্মণ, রোজা, অসিত হালদার, নামিদামি আরও অনেকে আছেন। লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়েও এগুলো মিলবে না।”
“কাপড়ের নীচের ছবিগুলোতে কি নতুন ফ্রেম লাগানো হয়ে গেছে?”
“হ্যাঁ।”
“ওগুলো ঝোলাবেন না?”
“এ দুটো হলেই কাজ শেষ। তারপর এক এক করে সবগুলোকে ঝোলাব ঠিক করেছিলাম। এখন এ দুটো নিয়ে যেতে পারব কিনা কে জানে!”
দীপকবাবু গম্ভীরভাবে বললেন, “ফ্রেম করলে ছবিগুলো যদি ভালো অবস্থায় থাকে, তাহলে নিয়ে যেতে পারেন।”
“বিদেশি ছবিগুলোও কি আপনিই ফ্রেম করেছেন?” আমি জিজ্ঞেস করলাম।
“না, ওগুলো ভালোভাবে ফ্রেম করা, তা ছাড়া এনভায়রনমেন্ট কনট্রোলড রুমে থাকে, নষ্ট হবার সম্ভাবনা প্রায় নেই।”
একেনবাবুর মনে হল হলঘরে যা দেখার তা হয়ে গেছে। বললেন, “চলুন স্যার, একটু বাইরে যাই।”
নীচের বারান্দাতেও কয়েকটা চেয়ার রয়েছে। সেখানেই আমরা এসে বসলাম।
“আচ্ছা স্যার, আপনার কাকা কি রাত্রে হিটার ব্যবহার করতেন?”
“হ্যাঁ, কাকা একদম ঠান্ডা সহ্য করতে পারতেন না। এই সময়ে রাত্রে বেশ ঠান্ডা পড়ে।”
“হিটারটা কি ইলেকট্রিক ছিল?”
“হ্যাঁ, কিন্তু ওটা গণ্ডগোল করছিল। কাকা খোঁজ করছিলেন কোনো ভালো কেরোসিন হিটার বাজারে আছে কিনা। পুরোনো একটা হিটার জোগাড় করেছিলেন কোনো বন্ধুর কাছ থেকে, কীরকম কাজ করে দেখতে।”
“কার কাছ থেকে স্যার?”
“তা বলতে পারব না।”
“আপনার কাকার মৃত্যু হয়েছে, কার্বন মনোক্সাইড পয়জনিং থেকে। আর ওটা বেরিয়েছে কেরোসিন হিটার থেকে।”
“হ্যাঁ, আমি শুনেছি। আরও কষ্ট হচ্ছে কেন জানেন? কাকাকে বলেওছিলাম চালানোর আগে হিটারটা চেক করে দেব।” আমাদের চোখে একটু বিস্ময় দেখে বললেন, “আমি নিজে কেরোসিন হিটার ব্যবহার করি। রাত্রে মাঝে মাঝেই লোডশেডিং হয়, ইলেকট্রিক হিটার তখন ইউজলেস। তাই একটা কার্বন মনোক্সাইড ডিটেক্টর কিনেছিলাম।”
“যে কোনো কারণেই হোক, আপনার কাকা স্যার আপনার চেক করার অপেক্ষায় থাকেননি।”
“আমারই অন্যায় হয়েছে। কাকার ভরসায় না থেকে আমারই মনিটরটা এনে চেক করা উচিত ছিল। কাকা একটু ভুলোমনাও। ইলেকট্রিক হিটারটা কি কাজ করছিল না?”
“কাজ করছিল,” দীপকবাবু উত্তর দিলেন।
“আশ্চর্য!” অজিতবাবু বিস্মিত।
“আচ্ছা স্যার, আপনি এর আগে এখানে কবে এসেছিলেন?”
“পরশু সন্ধের সময়। আমি, রঞ্জন, অনুরাধা- মানে রঞ্জনের স্ত্রী, সবাই এসেছিলাম। কাকাই ফোন করে আসতে বলেছিলেন। অনুরাধা আবার সবার জন্যেই রান্না করে এনেছিল।”
“এখান থেকে কখন আপনারা গেলেন?”
“রঞ্জনরা মনে হয় পৌনে দশটা নাগাদ চলে যায়, আমি তার একটু বাদেই যাই।”
“আরেকটু বাদে মানে ক’টার সময় স্যার?”
“ঠিক খেয়াল করিনি। হয়তো দশটা হবে। সাড়ে ন’টার সময় নিতাই দুধ নিয়ে এলে কাকা ওকে বললেন রঞ্জনদের বাসনপত্রগুলো ধুয়ে দিতে। ওরা তিন জন নীচে চলে গেলে কাকা হঠাৎ বললেন, বাড়ি থেকে যে ছবিগুলো চুরি হচ্ছে, আমি আমি সে বিষয়ে কিছু জানি কিনা! বলার ধরনটা খুব বাজে লাগল, কারণ কাকার ছবিগুলোতে শুধু আমিই হাত দিই।
“বললাম, কী যা-তা বলছ! কে চুরি করছে? আমি?”
“কাকা বললেন, “তুই কেন, আরও তো অনেকে আসে। তুই তো ছবি নামিয়ে প্যাক করে রাখছিস, সেখান থেকেই নিশ্চয় এক-আধটা চুরি হচ্ছে। … ঠিক আছে, যা।” বলে শুতে চলে গেলেন।
“এটা ঠিক, গত কয়েক মাসে আমি চব্বিশটা ছবি প্যাক করে রেখেছি। সেখান থেকেই দুটো করে নিয়ে যাই, নতুন ফ্রেম লাগিয়ে আবার প্যাক করেই ফেরত আনি। আমার প্ল্যান ছিল চব্বিশটা হয়ে গেলে প্যাকিং খুলে এক এক করে দেয়ালে ঝোলাব। কিন্তু কাকা হঠাৎ এই চুরি হবার কথা ভাবছে কেন? আমি একটু চিন্তিত হয়েই নীচে গিয়ে ছবিগুলো গুনলাম। সত্যিই দুটো ছবি মিসিং। মোট চব্বিশটা থাকার কথা বাইশটা রয়েছে! সর্বনাশ, গুনতিতে ভুল হয়নি তো? এদিকে রাত হয়ে যাচ্ছিল। রঞ্জনরা ইতিমধ্যে চলে গেছে। শান্তিনিকেতনের এই অঞ্চলে আটটার পরে রাস্তায় লোকজন থাকে না। সেদিন আর কোনো ছবি নিয়ে বেরোলাম না। ঠিক করলাম, ফিরে এসে আরেক বার গুনব, তারপর শেষ দুটো প্যাক করা ছবি ফ্রেম করতে নিয়ে যাব।”
“এখন কি এক বার গুনে দেখবেন স্যার?” একেনবাবু জিজ্ঞেস করলেন।
“আজকে? না, আজ থাক। আজকে ওই শেষ ছবি দুটো নিতে এসেছি। সেটা ফ্রেম করে লিস্ট মিলিয়ে দেখলেই আমার কাজ শেষ। এখন তো আর কাকা নেই। কার আর দুশ্চিন্তা!”
এই বলে অজিতবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে জিজ্ঞেস করলেন, “আর কোনো প্রশ্ন আছে কি?”
“আমার নেই স্যার,” বলে একেনবাবু দীপকবাবুর দিকে তাকালেন।
“আপনি যেতে পারেন। শুধু শান্তিনিকেতনের বাইরে কোথাও গেলে আমাদের জানিয়ে যাবেন।” দীপকবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন।
“যে দুটো ছবি নিয়ে যাচ্ছি, সেগুলো কয়েক দিনের মধ্যে ফেরত দিয়ে যাব, আপনার গার্ডদের বলে যাবেন যাতে সমস্যা না হয়।”
“বলে দেব।”
গেটের সামনে দেখলাম ছবি নিয়ে যাচ্ছেন বলে একজন গার্ড অজিতবাবুকে আটকেছে। দীপকবাবু হাত নেড়ে ছেড়ে দিতে বলতে যেতে দিল।
অজিতবাবু চলে যাবার পর একেনবাবু বললেন, “এক বার রঞ্জনবাবু আর সিদ্ধার্থবাবুর সঙ্গে কথা বলা যাবে কি?”
“নিশ্চয়। আমি রঞ্জনবাবুকে বলেও রেখেছি, তাঁকে এখন বাড়িতে পাওয়া যাবে। সিদ্ধার্থবাবুকেও খবর দেওয়া হয়েছে।”
নিতাই ইতিমধ্যে আমাদের জন্য চা আর বিস্কুট নিয়ে এল। কেউই আমরা চাইনি, বাড়িতে এটাই নিশ্চয় দস্তুর ছিল। ভালোই হল, চা পিপাসা একটু পেয়েছিল।
গাড়িতে উঠে একেনবাবু বললেন, “আচ্ছা দীপক, এক বার অজিতবাবুর দোকান হয়ে যেতে পারি কি?”
“নিশ্চয়।”
অজিতবাবুর দোকান, অজিত-ফোটো-ফ্রেমিং রতনপল্লির বাজারের প্রায় পাশেই। সামনে ছোটো কাউন্টার। সেখানে বসে অজিতবাবু কার সঙ্গে জানি ফোনে কথা শেষ করছিলেন। আমাদের দেখে উঠে এলেন, “আসুন, আসুন, কী মনে করে?”
“চলে এলাম স্যার, আপনার অপারেশন দেখতে। ডিস্টার্ব করলাম না তো?”
“আরে না, না, কী মুশকিল!” অজিতবাবু বললেন, “কাজগুলো হয় সব পেছনের ঘরে। দেখতে চান? আসুন।”
আমি চিরদিন দেখেছি লম্বা লম্বা কাঠের টুকরো, বোর্ড ইত্যাদি নিয়ে কাচ লাগিয়ে পেরেক ঠুকে ঠুকে মিস্তিরিরা ফ্রেম বানায়। পর্দা সরিয়ে যেখানে নিয়ে আমাদের ঢোকালেন, সেটা বড়োসড়ো একটা ঘর, যার অনেকটা জুড়ে দুটো ফোটো ফ্রেমিং মেশিন বসানো। কম্পিউটার চালিত কাটিং মেশিন, সেইসঙ্গে মেশিন বেড-এ বসানো হাবিজাবি বেশ কিছু গ্যাজেট, যেগুলোর নামও জানি না। ঘরের একদিকে একটা ডেস্ক আর চেয়ার। সেখানে একটা কম্পিউটার, প্রিন্টার আর কিছু কাগজপত্র
“এ তো এলাহি ব্যাপার স্যার। এই শান্তিনিকেতনে এরকম দামি দু-দুটো মেশিন?”
“দোকানটা শান্তিনিকেতনে, কিন্তু কাস্টম-মেড ফ্রেম আমি সারা ভারতবর্ষেই সাপ্লাই করি।”
“অ্যামেজিং স্যার, ট্রলি অ্যামেজিং… সত্যিই, আমি কিন্তু মুগ্ধ!”
একেনবাবুর বলার ভঙ্গিতে অজিতবাবু একটু মজাই পেলেন। স্মিতমুখে বললেন, “আপনাকে মুগ্ধ করা তো দেখছি সহজ ব্যাপার। এবার চলুন, আপনাকে আরও মুগ্ধ করার জন্য আমাদের এখানকার স্পেশাল চা খাওয়াই।”
“বেশ, কিন্তু এক সেকেন্ড স্যার, আপনার কম্পিউটারে কি ইন্টারনেট কানেকশন আছে?”
“হ্যাঁ, কেন বলুন তো?”
“একটা জরুরি ইমেল পাঠানোর ছিল, যদি ব্যবহার করতে পারতাম!”
“নিশ্চয়। ওটা অনলাইনেই আছে। গো অ্যাহেড।”
একটু আগেই চা খেয়েছি, কিন্তু চা এমন একটা বস্তু, ঘন ঘনই খাওয়া যায়। কাউন্টারের সামনে বসে চা খেতে খেতে গল্প করছি, একটু বাদেই একেনবাবু হাসি হাসি মুখে ফিরে এলেন।
“বাঃ দারুণ, খুব উপকার হল স্যার! বেশ স্পিড কিন্তু আপনার এখানকার কানেকশনে। একেবারে ফুস্ করে সব কিছু হয়ে গেল। যাই বলুন স্যার, এখানকার সাইবার কাফেগুলো নো গুড।”
“সেটা ঠিক, একটা লাইনে এত জনকে বসায় স্পিড-এর কোনো মা-বাপ থাকে না। …এদিকে আপনার চা তো ঠান্ডা হয়ে গেল, আরেক কাপ আনাই।”
“আরে না স্যার, এই ঠান্ডা চা-ই তো খাসা!” বলে একটা চুমুক দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, “আচ্ছা স্যার। এই যে এত ছবি আপনার এখানে, চুরি-টুরি হয় না?”
“না, আজ পর্যন্ত হয়নি। একটা বার্গলার অ্যালার্ম রেখেছি। একটা দারোয়ানও রাত্রে এইখানে ঘুমোয়। কলকাতার মতো শান্তিনিকেতনে অত চুরি হয় না।
“তাও… এত দামি দামি মেশিন, কম্পিউটার, ফ্রেমিং-এর যন্ত্রপাতি। মেটাল ফ্রেমগুলোর দামও তো কম নয়।”
“ফ্রেমগুলো রাত্রে এক বার গোনা হয়, সকালে আরেক বার। কোনোদিনই গরমিল হয়নি।”
“বাঃ, এদিকে অটোমেটিক মেশিন, কিন্তু ম্যানুয়াল কাউন্টিং। যাই বলুন স্যার, ম্যানুয়াল কাউন্টিং-এর থেকে ভালো কিছু নেই। একেবারে চোখে চোখে পরখ করা। হেরফের হলেই ধরা পড়ে যাবে।”
ইতিমধ্যে একজন কাস্টমার এসে যাওয়ায় আমরা আর বসলাম না, অজিতবাবুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সিদ্ধার্থবাবুর বাড়ির দিকে রওনা দিলাম।
সিদ্ধার্থবাবুর বাড়ি গুরুপল্লিতে। বাড়িতেই ছিলেন। দেখতে শক্ত-সমর্থ, কিন্তু বোঝা যায় বয়স হয়েছে। তার ওপর প্রিয় বন্ধুর মৃত্যুতে খুবই বিধ্বস্ত। বললেন, “বন্ধুদের মধ্যে ও-ই একমাত্র বেঁচে ছিল, আর তো সবাই চলেই গেছে। তিন দিন ওর কাছে যেতেও পারিনি, ফ্লু হয়েছিল। গতকাল অজিতের কাছ থেকে দুঃসংবাদটা শুনলাম। আচ্ছা, কী করে মৃত্যু হল বলুন তো? কার্বন মনোক্সাইড পয়জনিং— এটাই শুধু শুনেছি।”
“সেটাই আমরা বার করার চেষ্টা করছি স্যার… হত্যা না আত্মহত্যা। আপনি কি ডঃ রায়কে ডিপ্রেসড দেখেছিলেন?”
“একদমই নয়। তবে মৃত্যু-চিন্তা ওর ছিল। যার জন্য একটা উইল করেছিল কয়েক মাস আগে।”
“তাতে তো বেশিরভাগ টাকাই ভাগ্নেকে দিয়ে গিয়েছিলেন, তাই না স্যার?”
“তা দিয়ে গিয়েছিল। আসলে ওর বোনকে ও খুবই ভালোবাসত। কিন্তু সে প্রেম করে বিয়ে করল রুদ্ররই এক বন্ধুকে, রুদ্র যাকে একেবারেই পছন্দ করত না। ফিলিংসটা একেবারে ভাইস-ভার্সা। বোনের সঙ্গে যোগাযোগ সেই থেকেই ছিন্ন হল। তারপর তো রুদ্র বিদেশ চলে গেল। রঞ্জন যখন হাই স্কুলে পড়ে তখন রঞ্জনের মা, মানে রুদ্রের সেই বোন মারা গেল। মারা যাবার সময় রঞ্জনকে নিশ্চয় কিছু বলে গিয়েছিল, মায়ের মৃত্যুসংবাদ দিয়ে রঞ্জন রুদ্রকে একটা চিঠি দেয়। সেই থেকেই রুদ্রের সঙ্গে রঞ্জনের যোগাযোগ। যাই হোক, আমাকে রুদ্র লিখেছিল রঞ্জনের খোঁজখবর রাখতে। ওকে আমি স্নেহ করি। অজিতও আমার প্রিয় পাত্র… ওর বাবাকেও আমি চিনতাম ছেলেবেলা থেকে। রুদ্রর পিঠোপিঠি দাদা।”
“অজিতবাবুর বাবা কি বেঁচে আছেন স্যার?”
“না, মারা গেছে কয়েক বছর হল।”
“আর রঞ্জনবাবুর বাবা।”
“তার খবর আমি রাখি না। তবে রঞ্জন কথায় কথায় বলেছিল ওর বাবার ক্যান্সার হয়েছে। সেই নিয়ে একটু চিন্তা ছিল ছেলেটার। যদিও বাবাকে একেবারেই পছন্দ করত না, মা’র ওপর অত্যাচার করত। তবু নিজের বাবা তো! এটা নিয়ে আমি কোনো আলোচনা করিনি রুদ্রের সঙ্গে, আমি তো জানি রুদ্র ভগ্নিপতির ওপর কী ভীষণ চটা!”
সিদ্ধার্থবাবু একটু গল্প করতে ভালোবাসেন মনে হল। এলোমেলো আরও অনেক কথা বললেন। কোনোটাই দরকারি নয়, কিন্তু বৃদ্ধ ভদ্রলোক থামিয়েও দেওয়া যায় না।
রঞ্জনবাবুরা থাকেন পূর্বপল্লিতে। সুন্দর এক তলা বাড়ি। সামনে ছোট্ট একটা বাগান। বাগানের নীচু পাঁচিল বোগেনভেলিয়াতে ভরতি। শান্তিনিকেতনে এই ফুলটার খুব প্রাচুর্য দেখি। ভেতরের বাগান মানে সবই টবের ফুল। পুরো জায়গা জুড়ে অজস্র টব সাজানো। বারান্দাতে রঞ্জনবাবু আর রঞ্জনবাবুর স্ত্রী দু-জনেই বসেছিলেন। দু-জনেরই ছোট্টখাট্ট চেহারা, মেড ফর ইচ আদার। রঞ্জনবাবু পত্রিকা পড়ছিলেন। ওঁর স্ত্রী কিছু একটা বুনছিলেন। আমাদের দেখে দু-জনেই উঠে দাঁড়ালেন।
দীপকবাবুর সঙ্গে ওঁদের আগেই কথা হয়েছে বুঝলাম। আমাদের পরিচয় করিয়ে দিতেই বললেন, “আসুন মিস্টার সেন, আপনার কথা দীপকবাবু আমাকে বলেছেন। বাপিবাবু, প্রমথবাবুর কথা অবশ্য বলেননি। খুব ভালো লাগছে সবার সঙ্গে পরিচয় হয়ে। আর হ্যাঁ, ইনি হচ্ছেন আমার স্ত্রী অনুরাধা।”
অনুরাধা ব্যস্ত হয়ে ভেতরে যাচ্ছিলেন… মনে হল অতিথি আপ্যায়ন করতে। একেনবাবু বললেন, “ম্যাডাম, আপনি বসুন।”
“একটু চা-তো খাবেন?”
“না। ম্যাডাম, কিচ্ছু খাব না। শুধু দুয়েকটা প্রশ্ন ছিল, সেগুলো করে চলে যাব।”
“তা হয় নাকি! এই প্রথম এলেন আমাদের বাড়িতে।”
“একটু আগেই আমরা দু-কাপ চা খেয়ে এসেছি।” আমি বললাম।
এই কথায় কাজ হল। কয়েকটা চেয়ার ইতিমধ্যেই এসে গিয়েছিল ভেতর থেকে। সবাই বসলাম। যে পত্রিকাটা সামনে টুলের ওপর রাখা, সেটা গতকালের পত্রিকা। একেনবাবুও খেয়াল করেছেন, পত্রিকাটা তুলে নিয়ে বললেন, “এটা তো স্যার কালকের পত্রিকা!”
“তাই নাকি!” তারপর তারিখটা দেখে রঞ্জনবাবু বললেন, “তাই তো! আসলে মামার খবরটা জানার পর থেকে কিছুতেই মন বসছিল না। পত্রিকা জমে ছিল, খেয়ালই করিনি পুরোনোটা তুলেছি।”
“কখন জানলেন স্যার ওঁর মৃত্যুর খবর?”
“অজিতদা ফোন করেছিলেন গতকাল সকালে। তার পর পরই সিদ্ধার্থমামা ফোন করেন। অনু শুনেই কান্নাকাটি শুরু করে। ও মামাকে খুব ভালোবাসত। মামাও অনেক স্নেহ করতেন ওকে। খবরটা শুনে আমরা দু-জনেই যাই মামার বাড়িতে। কিন্তু পুলিশ আটকায়। তখনই শুনি সম্ভবত কেরোসিন হিটারের কার্বন মনোক্সাইড থেকে পয়জনিং হয়েছে। সেই থেকেই নিজেকে খুব অপরাধী লাগছে।”
“কেন বলুন তো স্যার?”
“মামা একটা কেরোসিন হিটারের খোঁজ করছিলেন জেনে হিটারটা আমিই দিয়েছিলাম। আমাদের বাড়িতেই ওটা ছিল, ভালো কাজ করত। তবে আমরা ঘরে একটা জানলা খোলা রাখতাম সবসময়।”
“আপনার মামা কি স্যার জানতেন যে কেরোসিন হিটার থেকে কার্বন মনোক্সাইড বেরোনোর সম্ভাবনা থাকে?”
“খুব ভালো করেই জানতেন। আমাকে বলেওছিলেন যদি ব্যবহার করেন, তাহলে একটা কি দুটো জানলা খুলে রাখবেন।”
“আই সি। আচ্ছা স্যার, আপনার মামার যে একটা উইল আছে সেটা কি আপনি জানেন?”
“আগে জানতাম না। ক’দিন আগে সিদ্ধার্থমামা বললেন।”
“আপনার জন্য তাতে কি কিছু ছিল স্যার?”
উত্তরটা দিতে রঞ্জনবাবু অস্বস্তিবোধ করলেন। একটু আমতা আমতা করে বললেন, “উইলটা আমি দেখিনি।”
“তা বুঝলাম, কিন্তু আপনি এ বিষয়ে কিছু শোনেননি?”
“সিদ্ধার্থমামা বলছিলেন, মামা আমার নামেই বেশিরভাগ সম্পত্তি রেখেছেন। শুনে খারাপই লেগেছিল আমাদের। খুব সাধারণভাবে আমরা থাকি, প্রয়োজনও আমাদের কম।”
“আপনার মামা এ নিয়ে কিছু বলেননি আপনাকে বলেছিলেন কি?”
“না।”
“যে রাতে আপনার মামা মারা যান সেদিন সন্ধেতে আপনারা তো গিয়েছিলেন মামার কাছে?”
“হ্যাঁ, মামা আমাদের আর অজিতদাকে ডেকেছিলেন ফ্যামিলি ডিনারের জন্যে।”
“তখনও কোনো কথা হয়নি উইল নিয়ে… মানে অজিতবাবুও উইল নিয়ে কোনো কথা তোলেননি, তাই তো?”
“হ্যাঁ, তাই।”
“কতক্ষণ ছিলেন স্যার ওখানে?”
“মামা সাড়ে ন’টার সময়ে শুতে চলে যান। তার কিছুক্ষণ বাদেই আমরা চলে আসি।”
“কিছুক্ষণ বাদে বলতে স্যার- কতক্ষণ?”
“আমরা আরও মিনিট দশেক ছিলাম।”
“আচ্ছা, আপনার মামা কোনো কারণে ডিপ্রেসড ছিলেন কি?”
“একেবারেই না, খুবই মুডে ছিলেন- অনেক গল্প করলেন। নিতাই যখন দুধ নিয়ে এল, তখন বললেন, ‘দুধটা রাখ, আমি বাথরুম থেকে এসে খাব। তুই বরং খাবারের বাসনপত্র, কাপ-প্লেট সব ধুয়ে রঞ্জন আর বৌমার গাড়িতে তুলে দে।” তারপর নামা বাথরুমে গেলেন। আমরা দু-জনে নিতাইকে কাপ-ডিশগুলো নীচে নিয়ে যেতে সাহায্য করলাম। কাপ-ডিশ ধোওয়ার সিংকটা নীচে।”
এটা শুনে আমাদের চোখে একটু বিস্ময় দেখে বললেন, “আসলে ডাইনিং রুমটা নীচেই ছিল। মামা খাবার জন্যে নীচে আসতে চাইতেন না বলে ওপরে রাখার জন্য একটা ডাইনেট সেট কিনেছিলেন। সেখানেই একা একা বা আর কেউ থাকলে তাদের সঙ্গে বসে খেতেন।”
“বুঝলাম স্যার, বলুন যা বলছিলেন।”
“বলছি, …খানিক বাদেই অজিতদা নীচে এলেন। দুধের গ্লাসটা নিতাইকে দিয়ে বললেন, কাকা শুতে চলে গেছেন। আমরা যখন চলে আসছি, হঠাৎ খেয়াল হল, মোবাইলটা খাবার টেবিলে ফেলে এসেছি। ওটা নিতে যখন ওপরে গেলাম, কাকার ঘরের দরজা তখন বন্ধ।”
“তখন ক’টা বেজেছিল স্যার?”
“এক্স্যাক্ট সময় বলতে পারব না, তবে পৌনে দশটার আগেই।”
“অজিতবাবু তখনও ছিলেন?”
“হ্যাঁ, অজিতদা নীচে কতগুলো ছবির ফ্রেম প্যাক করছিলেন। উনি বেশ কিছু ছবি নতুন করে ফ্রেম করছিলেন ছবিগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বলে।”
“মামার ছবিগুলো আপনি দেখেছেন স্যার?”
“সত্যি বলতে কী, তেমনভাবে দেখিনি। আসলে আমার বা অনুর ছবির ব্যাপারে কোনো ইন্টারেস্টং নেই। ওটা মামা আর অজিতদার জগৎ।”
“আই সি।”
“আচ্ছা, আপনি কি মামার মৃত্যুটা অ্যাক্সিডেন্ট বলে মনে করছেন না?” রঞ্জন হঠাৎ প্রশ্নটা করলেন।
“কেন বলুন তো স্যার?”
“আসলে এমনভাবে সময় ইত্যাদি নিয়ে প্রশ্ন করছেন… আমার কেমন জানি মনে হচ্ছে, আপনি এর মধ্যে কোনো ফাউল প্লে দেখছেন!”
“কী যে বলেন স্যার, এ ধরনের যে কোনো মৃত্যুরই একটু অনুসন্ধান করতে হয়— এটা সেটাই। …ঠিক আছে স্যার, আপনাকে আর বিরক্ত করব না। আজকে চলি।” এই বলে রঞ্জনবাবুকে একটু হতচকিত করেই উঠে পড়লেন একেনবাবু। আমাদের কথাবার্তার মধ্যে অনুরাধা ভেতরে গিয়েছিলেন, এক প্লেট মিষ্টি নিয়ে ফিরলেন।
“এ কী, চলে যাচ্ছেন! একটু মিষ্টিমুখ করে যান?”
“আজ নয় ম্যাডাম, আরেক দিন।”