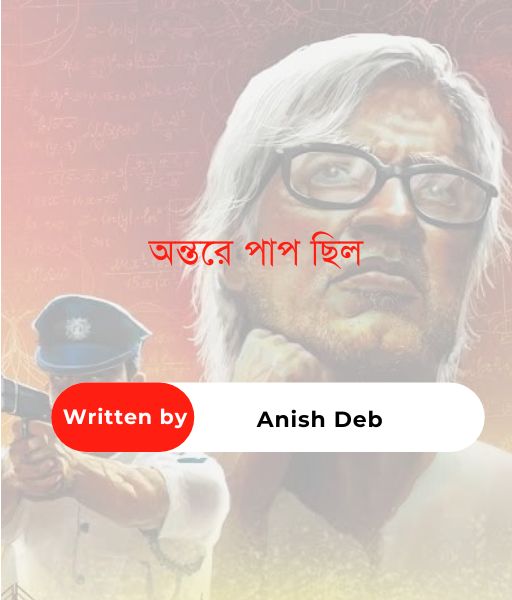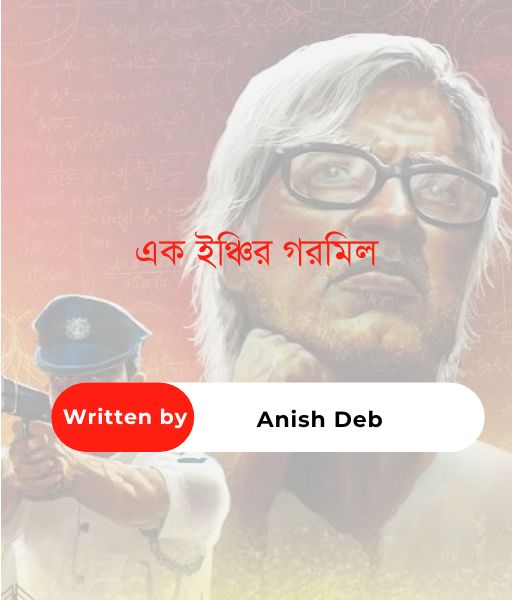ধুলো উড়িয়ে বাসটা
‘প্রতিঘাত’ উপন্যাসের প্রথম পর্ব ‘কিশোর ভারতী’ পত্রিকার ২০১৬ সালের পুজোসংখ্যায় প্রকাশিত হয়। প্রথম পর্ব প্রকাশিত হওয়ার কারণ লেখাটি আমি শেষ করতে পারিনি। এরকম ‘দুর্ঘটনা’ আগেও কয়েকবার ঘটেছে—এবং এই ‘কিশোর ভারতী’ পত্রিকাতেই। এর জন্য দায়ী আমি। কারণ, গল্প বা উপন্যাসের প্লট আমার মাথায় আসে দেরিতে এবং আমার লেখার গতির এমনই হাল যে, তাকে গতি না বলে ‘দুর্গতি’ বললেই ভালো মানায়।
এই আংশিক উপন্যাস প্রকাশের ব্যাপারে ‘কিশোর ভারতী’-র সম্পাদক ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় যে-দুঃসাহস দেখিয়েছেন তার কোনও তুলনা হয় না। তাঁকে সেলাম জানাই। সেইসঙ্গে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতাও। বারবার এভাবে লেখা প্রকাশের সুযোগ দেওয়ার জন্য।
২০১৬-তে প্রথম পর্ব প্রকাশের পর ২০১৭ সালের জানুয়ারি মাস থেকে ‘কিশোর ভারতী’-র পাতায় ‘প্রতিঘাত’-এর বাকি অংশের ধারাবাহিক প্রকাশ শুরু হয়। ২৮টি কিস্তিতে লেখাটি শেষ হয় ২০১৯ সালের, মানে এবছরের, সেপ্টেম্বর মাসে। বই প্রকাশের সময় উপন্যাসটির নামকরণ করা হয় ‘প্রতিঘাত সম্পূর্ণ’—এটা বোঝানোর জন্য যে বইটি ‘প্রতিঘাত’ উপন্যাসের আংশিক প্রথম খণ্ড নয়, সম্পূর্ণ উপন্যাসটিই বই হয়ে বেরিয়েছে। এবং বই হয়ে বেরোনোর আগে আমি সাধ্যমতো ঘষামাজা করেছি।
‘প্রতিঘাত সম্পূর্ণ’ এখন আপনার হাতে। পাঠক হিসেবে আপনার বিচারই হল শেষ বিচার। সেই বিচারের অপেক্ষায় রইলাম। ইতি—
অনীশ দেব
৭ অক্টোবর, ২০১৯
ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট
অ্যাডামাস ইউনিভার্সিটি
কলকাতা ৭০০১২৬
ধুলো উড়িয়ে বাসটা একটা স্টপেজে এসে দাঁড়াল। বিকেলটা তখন মসৃণভাবে সন্ধের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। কন্ডাক্টর জোরে-জোরে দুবার হাঁক দিল, ‘বটতলা। বটতলা!’
কত যে ‘বটতলা’ আছে এ-রাজ্যে! গ্রাম, টাউন, শহর—কোথাও ‘বটতলা’-র কমতি নেই। রোশন ভাবল।
একটানা ঘণ্টাখানেক দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে আসার পর এই মিনিট-কুড়ি-পঁচিশ আগে ও একটা বসার জায়গা পেয়েছে। বলতে গেলে সেই হাওড়া থেকেই বাসে ঠাসা ভিড়—সবসময় যেমনটা হয়।
জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রোশনের খারাপ লাগল না। গাছপালা, দূরের ছোট-ছোট দু-চারটে ঘরবাড়ি আর বিস্তীর্ণ চাষের জমিতে কেমন একটা প্রশান্তি ছেয়ে আছে।
‘এই জায়গাটার নাম কী, কাকু?’ পাশে বসা রোগামতন প্রৌঢ় মানুষটিকে জিগ্যেস করল রোশন।
ভদ্রলোক বোধহয় লজেন্স চুষছিলেন, কারণ ওঁর ডানদিকের গালটা ফুলে ছিল। অবশ্য মাড়ির সমস্যাও হতে পারে।
রোশনের প্রশ্নে গালফোলাটা কমে গেল। মানে, মাড়ি নয়—লজেন্স।
তারপর জবাব দিলেন, ‘আহাউর।’
রোশন একটু ঘাবড়ে গেল। এরকম নাম আবার হয় না কি! ও অবাক চোখে ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করল, ‘কী বললেন?’
প্রৌঢ় লজেন্সটাকে মুখে নাড়াচাড়া দিয়ে সাইড করলেন। তারপর বললেন, ‘বললাম তো, আশাপুর—।’
আশাপুর! নামটার মধ্যে কেমন যেন একটা টান আছে।
কোলে রাখা কালো রঙের ব্যাকপ্যাকটা হাতে নিয়ে সিট ছেড়ে উঠে পড়ল রোশন। ভিড় ঠেলে এগোতে-এগোতে চেঁচিয়ে বলল, ‘বেঁধে! বেঁধে! কন্ডাক্টরভাই, নামব। বটতলায় নামব…।’
বাসের চাকা গড়াতে শুরু করেও আবার থমকে দাঁড়াল। অধৈর্য ড্রাইভার দুবার ‘প্যাঁ—প্যাঁ—’ করে হর্ন বাজাল।
দরজার কাছাকাছি এসে বাড়তি ভিড় ঠেলেঠুলে অবশেষে রোশন নামতে পারল। ওর গায়ে তখন বিচিত্র ঘামের গন্ধ। কারণ, ওর নিজের ঘামের গন্ধের সঙ্গে মিশে গেছে অন্যান্য মানুষের ঘামের গন্ধ।
বাসটাকে ধুলো উড়িয়ে চলে যেতে দেখল রোশন। তারপরই হাইরোডে ও একা।
এবার চোখ মেলে আশাপুরকে দেখল।
সামনে সবুজ ধানখেত। তার মধ্যে কয়েকটা বড়-বড় গাছ ডালপালা শূন্যে ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দুটো গাছের ফাঁক দিয়ে তাকালে চোখে পড়ছে রংচঙে আকাশ। সেই রঙিন পটভূমিতে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। আশাপুরে রোশনের দেখা প্রথম সূর্যাস্ত।
সূর্য যখন অস্ত যায় তখন রোশনের মনে ভয় হয়—যদি পরদিন না ওঠে! কিন্তু প্রকৃতির নিয়মে কোনও হেরফের হয় না। সূর্য ঠিক সময়মতো উঠে পড়ে পরদিন।
অথচ মানুষ? মানুষ যখন বিছানায় অস্ত যায় তখন? পরদিন কি সে নিয়ম করে আবার উঠে বসে বিছানায়? মোটেই না।
মায়ের কথা মনে পড়ল রোশনের। মা বড় করুণভাবে অস্ত গিয়েছিল। তখন রোশন মায়ের পাশে থাকতে পারেনি। অথচ রোশন ছাড়া মায়ের আর কোনও কাছের মানুষ ছিল না।
রোশন মায়ের পাশে থাকতে পারেনি, কারণ, রোশন তখন জেলে বন্দি ছিল। বিনা দোষে।
মায়ের কথা মনে পড়তেই চারপাশে এক অদ্ভুত শূন্যতা টের পেল। এবং সেই শূন্যতার সঙ্গে একটা ভয়। একা হয়ে যাওয়ার অচেনা ভয়। সেই অচেনা ভয় শীতের চাদরের মতো ওকে আদর করে জড়িয়ে ধরে। যেন সে কোনও পরম বন্ধু, কোনও ঘনিষ্ঠ আত্মীয়।
রোশন চুপচাপ দাঁড়িয়ে সূর্যের মৃত্যু দেখল। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল ওর বুকের ভেতর থেকে।
বেলাশেষের আলোয় ও দেখল, ধানখেতের দূরের সীমানায় দাঁড়িয়ে রয়েছে বেশ কিছু গাছপালা। তার ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ছে কয়েকটা ছোট-বড় ঘর। সেগুলো পেরিয়ে দু-চারটে পাকাবাড়ি। সেইসব বাড়ির মাথায় ডিশ অ্যান্টেনা দেখা যাচ্ছে।
হাইরোড দিয়ে কয়েকটা লরি, ট্রাক আর প্রাইভেট কার ছুটে গেল। রোশন সেগুলোকে যেন দেখেও দেখতে পেল না।
‘যেদিকে দু-চোখ যায়’ এ-কথা ভেবেই কলকাতা ছেড়েছিল ও। কারণ, ও ভুলতে চেয়েছে মায়ের শোক আর জেলের জঘন্য এপিসোড। এখন দেখা যাক, আশাপুর ওর মন ভোলাতে পারে কি না। না হলে কাল সকালে আবার ‘যেদিকে দু-চোখ যায়’।
বটতলা বাস স্টপেজে সত্যি-সত্যিই বটগাছ রয়েছে। তাও আবার একটা নয়, দুটো। একটা রোশন রাস্তার যেদিকে দাঁড়িয়ে আছে সেদিকে, আর-একটা উলটোদিকে—কিছুটা বাঁ-দিকে সরে গিয়ে।
সেই বটগাছটার গা ঘেঁষে একটা চায়ের দোকান—চাটাই আর বাঁশের খুঁটি দিয়ে তৈরি।
রোশন দু-দিকে একবার করে দেখে নিয়ে হাইরোড পার হল। তারপর পায়ে-পায়ে এগোল চায়ের দোকানের দিকে।
দোকানের তিন-চার হাতের মধ্যেই একটা ঢালু পিচ রাস্তা ঢুকে গেছে আশাপুরের দিকে। রাস্তাটার বাঁ-দিক ঘেঁষে পরপর তিনটে পাকা দোকানঘর। প্রথমটা টায়ারের দোকান। দোকানের বাইরে পুরোনো টায়ারের ডাঁই—বাসের টায়ার আর সাইকেলের টায়ার। তার পাশে টায়ার সারানোর সরঞ্জাম।
টায়ারের দোকানের পাশের দুটো দোকান এখন বন্ধ। তবে সাইনবোর্ড দেখে বোঝা যায়, একটা সেলুন, আর একটা মোবিল, গিয়ার অয়েল ইত্যাদি বিক্রির দোকান।
রোশন চায়ের দোকানের বেঞ্চে গিয়ে বসল। ব্যাকপ্যাকটা পিঠ থেকে খুলে পাশে রাখল। এক গ্লাস চা আর দুটো বিস্কুট চাইল।
অন্য আর-একটা বেঞ্চে আরও দুজন খদ্দের বসে ছিলেন। তাঁদের হাতে চায়ের গ্লাস—মাঝে-মাঝে চুমুক দিচ্ছেন। দেখে বোঝা যায়, লোকাল লোক। দোকানি ভদ্রলোক তাঁদের সঙ্গে টুকটাক কথা বলছিলেন।
রোশন বেঞ্চে বসতেই দোকানি ওর দিকে ফিরে তাকিয়েছেন। রোশন চা-বিস্কুটের অর্ডার দিতে তিনি বললেন, ‘এখনই দিচ্ছি।’ তারপর দু-চার সেকেন্ড সময় নিয়ে জিগ্যেস করলেন, ‘কোত্থেকে? কলকাতা থেকে আসছেন?’
‘হ্যাঁ—।’ রোশন জানে, ওর পোশাক-আশাক আর বডি ল্যাঙ্গুয়েজে শহুরে ছাপ স্পষ্ট।
ও দোকান আর দোকানিকে খুঁটিয়ে দেখছিল।
দোকান এবং দোকানি দুজনেরই বয়েস হয়েছে। ধোঁয়ায়-ধোঁয়ায় দোকানের চাটাইয়ের দেওয়াল, সিলিং সব কালো হয়ে গেছে। নানান কোণে ঝুল জমেছে। দোকানের ভেতরে-বাইরে খদ্দেরদের জন্য কয়েকটা বেঞ্চ পাতা রয়েছে। এ ছাড়া দোকানের ভেতরে ছোট মাপের দুটো খাটো টেবিল। একটা লাট খাওয়া খবরের কাগজ দুটো টেবিলে তিন-চারভাগে ছড়িয়ে পড়ে আছে।
দোকানের বাইরের দিকে পাতা উনুন। উনুন থেকে খানিকটা দূরে চাটাইয়ের দেওয়ালে দুটো কাঠের তাক। সেখানে বিস্কুটের বোয়েম সাজানো। আর তার নীচের তাকে অল্পবিস্তর সিগারেট, বিড়ি আর দেশলাইয়ের আয়োজন।
দোকানির মাথায় টাক, রোগা চেহারা, গালে খোঁচা-খোঁচা কাঁচাপাকা দাড়ি, গায়ের রং তামাটে। চোখে চশমা। পোশাক রঙিন চেক লুঙ্গি আর হাতাওয়ালা গেঞ্জি। গেঞ্জির বগলের কাছে বেশ কয়েকটা ছোট-বড় ফুটো।
দোকানি দুটো বিস্কুট রোশনের হাতে দিলেন। তারপর চায়ের গ্লাসে চিনি দিয়ে চামচ নাড়তে-নাড়তে জিগ্যেস করলেন, ‘তা এই আশাপুরে কী জন্যে? কোনও কাজে এলেন?’
এ-প্রশ্নটা যে ওকে কেউ না কেউ করবেই এটা রোশন জানত। তাই উত্তর ভাবাই ছিল মনে-মনে। ও জানে যে, ও যদি বলে, বাসের জানলা দিয়ে জায়গাটা দেখে ওর ভালো লেগে গেছে, তাই ও আশাপুরে নেমে পড়েছে, তা হলে কেউই ওর কথা বিশ্বাস করবে না। বরং ওকে সন্দেহের চোখে দেখবে।
আসলে জায়গাটার নাম হতাশাপুর হলেও রোশন নেমে পড়ত। জায়গাটা চোখে ধরেছে বলে।
‘হ্যাঁ—একটা কাজ নিয়েই এসেছি। আমি ”সুপ্রভাত” খবরের কাগজের রিপোর্টার।’ কথা বলতে-বলতে হাত বাড়িয়ে চায়ের গ্লাসটা নিল : ‘পশ্চিমবঙ্গের বারোটা জায়গা আমি বেছে নিয়েছি। সেইসব জায়গায় বিখ্যাত যেসব জিনিস আছে—মানে, স্পেশাল যেসব জিনিস আছে—সেগুলো নিয়ে আমি একটা লেখা তৈরি করছি। সামনের মাস থেকে ওটা প্রতি সপ্তাহে ধারাবাহিকভাবে বেরোবে।’ চায়ে দুবার চুমুক দিয়ে ‘আ—আঃ!’ করে আরামের শব্দ করল। তারপর বলল, ‘কাকু, চা-টা হেবি হয়েছে। আচ্ছা, আপনার দোকানে কি ”সুপ্রভাত” কাগজ রাখেন?’
‘না, রাখি না।’
উত্তরটা রোশন জানত, কারণ, টেবিলে পড়ে থাকা কাগজের নামটা ও আগেই লক্ষ করেছে।
রোশন যখন কথা বলছিল তখন বাকি দুজন খদ্দের ওর দিকে আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে ছিল। ও বিস্কুটে কামড় দিল, চায়ে চুমুক দিল কয়েকবার। তারপর দোকানদারকে জিগ্যেস করল, ‘এখানে স্পেশাল সেরকম কিছু আছে নাকি?’
দোকানদার ভদ্রলোক কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার আগেই একজন খদ্দের বলে উঠলেন, ‘আশাপুরে বিখ্যাত কালীমন্দির আছে—জগন্ময়ী কালীমন্দির। একশো উনত্রিশ বছরের পুরোনো।’
রোশন ভদ্রলোকের দিকে তাকাল। মুখে-চোখে সাংবাদিকের আগ্রহ ফুটিয়ে তুলে বলল, ‘তাই নাকি? একশো উনত্রিশ বছরের পুরোনো! এটার খবর তো কেউ জানেই না! অন্তত আমি তো কখনও শুনিনি! এটার কথা তো লিখতেই হবে! কীভাবে ওই মন্দিরে যেতে হয় একটু বলুন না…।’
তখন খদ্দের দুজন ভাগাভাগি করে মন্দিরের পথের হদিশ বলতে লাগল।
ব্যাকপ্যাকের চেন খুলে ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দিল রোশন। একটা প্যাড আর পেন বের করে নিল। এবং চায়ের গ্লাস বেঞ্চে নামিয়ে রেখে জগন্ময়ী কালীমন্দিরের ডিরেকশন নোট করে নিতে লাগল।
আলো ক্রমে কমে আসছিল। দোকানদার সুইচ টিপে দোকানের আলো জ্বেলে দিল। দুটো সাধারণ বালব। তবে এইটুকু দোকানের পক্ষে যথেষ্ট।
দোকানদার ধূপকাঠি জ্বেলে ঠাকুরের আসনের সামনে কয়েকবার ঘুরিয়ে মাথায় ঠেকিয়ে চাটাইয়ের দেওয়ালে গুঁজে দিল।
একটা এরোপ্লেন উড়ে গেল আকাশপথে। বেঞ্চে বসেই প্লেনের রঙিন আলোগুলো দেখতে পেল রোশন। আকাশের দিকে তাকিয়ে ও ভাবতে লাগল। এখন ও কী করবে? মন্দিরের ডিরেকশন লিখে নেওয়ার কাজ শেষ। অর্থাৎ, সাংবাদিকের অভিনয়ের পালা আপাতত শেষ। এবার হোটেল-ফোটেলের খোঁজ করা দরকার। কারণ, রাতটা তো কাটাতে হবে! শুধু একটা রাত নয়, হয়তো পরপর বেশ কয়েকটা রাত। অন্তত যতদিন আশাপুরে ওর থাকতে ভালো লাগে, যতদিন মন টিকে যায় এখানে।
চারপাশে ছাই রঙের অন্ধকার। হাইরোড ধরে যেসব গাড়ি এদিক-ওদিক যাওয়া-আসা করছে তাদের হেডলাইটের আলোর পিছনে ভালো করে কিছু দেখা যাচ্ছে না। মাঝে-মাঝে দু-একটা সাইকেল, গাড়ি, মোটরবাইক অথবা সাইকেল-রিকশা চায়ের দোকানের পাশের রাস্তাটা দিয়ে আশাপুরের দিকে চলে যাচ্ছে, কিংবা বেরিয়ে আসছে হাইরোডের দিকে। আর থেকে-থেকে নানারকম হর্নের শব্দ।
রোশন চায়ের দোকানির দিকে তাকিয়ে বলল, ‘আপনাদের আশাপুর বেশ ব্যস্ত জায়গা দেখছি—।’
দোকানদার ভদ্রলোক কখন যেন একটা টুলের ওপর বসে পড়েছিলেন এবং একটা বিড়ি ধরিয়ে ফেলেছিলেন। বিড়িতে আয়েস করে একজোড়া টান দিয়ে ‘খকখক’ করে কয়েকবার কাশলেন। তারপর বললেন, ‘আশাপুরকে আপনি কি গ্রাম-টাম ভাবলেন নাকি? এটা টাউনের চেয়েও বেশি কিছু। এখানে অনেক ঘরে ছোট-ছোট লেদ কারখানা আছে। একটা সুতোকল আছে। জলের ট্যাঙ্কি তৈরির ফ্যাক্টরি আছে। আরও ছোট-ছোট কত কিছু!’
‘তা হলে তো ছোট-বড় গোলমালও লেগে আছে…।’
‘আছে—তাতে কী! আমরা বেশ আছি…।’ কথাটা শেষ করেই দোকানি কেমন যেন একটা ইশারা করলেন রোশনকে। একটা চোখও টিপলেন—তবে খদ্দের দুজনকে আড়াল করে। দুবার কেশে নিয়ে বললেন, ‘আপনি তো হালকা মনে ঘুরতে বেরিয়েছেন—তেমন কোনও তাড়া নেই। তা আরও এক-দু-কাপ চা-টা খান—আপনাকে আরও অনেক গল্প শোনাব…।’
রোশন আর-এক গ্লাস চায়ের অর্ডার দিল। মনে-মনে ভাবল, এই দোকানদার ভদ্রলোকের কাছ থেকেই না হয় থাকার হোটেলের হদিশ জেনে নেওয়া যাবে। তা ছাড়া এই ভদ্রলোক রোশনকে আরও অনেক গল্প শোনাতে চান। রোশন সেসব গল্প শোনার জন্য তৈরি। ও এখন এলোমেলো ভবঘুরে—তাই এলোমেলো গল্প শোনাটাই ওর জীবন। যে-জীবনটার এখন কারও কাছে কোনও মূল্য নেই। এমনকী ওর নিজের কাছেও।
আরে, কী সুন্দর একটা চাঁদ উঠেছে!
হঠাৎই আকাশের দিকে নজর চলে গেছে রোশনের। সেখানে একটা ফাটাফাটি আধখানা চাঁদ। আধখানা, তাও কী সুন্দর! তা হলে অর্ধেক জীবনও তো একটা সুন্দর জীবন হতে পারে।
রোশন কোথায় যেন হারিয়ে গেল।
দোকানদার ‘কাকু’-র কথা কানে আসতেই ও আবার চায়ের দোকানে ফিরে এল।
খদ্দের দুজন তখন বেঞ্চ ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। একজন বাঁ-হাতে বাঁধা ঘড়ি দেখল। তারপর অপরজনকে বলল, ‘না, ভাই, চলো—উঠি। আরও বসলে দেরি হয়ে যাবে।’
‘হ্যাঁ, সাতটা পেরিয়ে গেলে রতনমোহনকে আর পাওয়া যাবে নাকো…।’
ওরা দুজন চলে গেল।
এবার দোকানদার ভদ্রলোক টুল ছেড়ে রোশনের কাছাকাছি এসে বসলেন। হাতের বিড়িতে শেষ কয়েকটা মরণ টান দিয়ে বললেন, ‘তখন লোকজন ছিল বলে বলতে পারিনি। মানে…।’ ভদ্রলোক ইতস্তত করতে লাগলেন। কয়েকবার মাথাও চুলকোলেন। বিড়ির ছোট হয়ে যাওয়া টুকরোটা হাইরোডের দিকে ছুড়ে ফেললেন।
রোশনের কপালে ভাঁজ পড়ল। ভদ্রলোক কি টাকা-ফাকা ধার চাইবেন নাকি? এরকম দোনামনা করছেন কেন?
কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ও বলল, ‘কী বলবেন, কাকু, বলুন না…।’
‘জগন্ময়ী কালীমন্দির ছাড়াও আমাদের এই আশাপুরে দেখবার মতো আরও একটা জিনিস আছে। মানে, বেশ অদ্ভুত টাইপের জিনিস। আর কোথাও এরকম হয়-টয় বলে মনে-টনে হয় না…।’
‘কী জিনিস?’ রোশনের কপালে ভাঁজ পড়ল।
‘লড়াই।’ চাপা গলায় দোকানকাকু বললেন, ‘এরকম লড়াই আপনি আগে কখনও দেখেননি। ব্যাপারটা নিয়ে খুব চাপাচাপি। এটার কথা সবাই জানে, তবে কেউ নাম মুখে নেয় না। দারুণ খেলা। লড়াইয়ের খেলা। বাজি ধরে লড়াই। মানে, লড়াইয়ের বাজি…।’
‘কোথায় হয় সেটা?’ কৌতূহল ফুটে উঠল রোশনের গলায়। বাজি ধরে লড়াই তো অনেক জায়গাতেই হয়! সেটাকে অদ্ভুত টাইপের বলার তো কোনও মানে হয় না!
দোকানদার ভদ্রলোক সতর্ক নজরে এদিক-ওদিক একবার দেখে নিলেন। তারপর একইরকম চাপা গলায় বললেন, ‘আপনি রিপোর্টার—তাই বলছি…। তবে দেখবেন, আমার নাম কোথাও যেন ফাঁস না হয়…।’
রোশন আশ্বাস দিল যে, ভদ্রলোকের নাম কোথাও ও জড়াবে না। কারণ, এটাই রিপোর্টারদের নীতি : খবরের সোর্সের নাম-ধাম কখনও তারা ফাঁস করে না। তা ছাড়া রোশন ওই জগন্ময়ী কালীমন্দির ছাড়া আশাপুরের আর কোনও ব্যাপার নিয়ে ‘সুপ্রভাত’-এ লিখবে না।
তখন দোকানদার ভদ্রলোক ওকে ‘অকুস্থল’-এর হদিশ দিলেন।
মেন রোড দিয়ে ঢুকে খানিকটা পথ গেলে বাঁ-দিকে একটা পিচরাস্তা পাওয়া যাবে। ভীষণ আঁকাবাঁকা রাস্তা। তবে কলাবতী নদীর কথা বললে সবাই পথ দেখিয়ে দেবে। কারণ, আশাপুরের গা ঘেঁষেই বয়ে চলেছে কলাবতী নদী। সেখানে নৌকো চলে, জেলেরা জাল ফেলে মাছ ধরে। তো লড়াইয়ের জায়গাটা হচ্ছে ওই কলাবতী নদীর ধারে—একটা মেগা সাইজের টিনের চালার ভেতরে। বাইরে থেকে মাঝে-মাঝে চিৎকার-চেঁচামেচি শোনা যায়।
‘প্রতি শনিবার রাতে লড়াইয়ের আসর বসে। যারা লড়াই দেখতে ভেতরে ঢোকে তাদের জন্যে বিশ টাকা করে টিকিট। আর যারা লড়াইয়ে নাম লেখায় তাদের কোনও পয়সা লাগে না—ফ্রি।’ কথাগুলো বলতে-বলতে দোকানদার ‘কাকু’-র চোখ দুটো বড়-বড় হয়ে গেল। তারপরই তিনি দু-চোখ সরু করে গলা নামিয়ে বললেন, ‘ভাই, আজ তো শনিবার—যদি রাতে সময় থাকে তো দেখে আসুন! একটা নতুন জিনিস দেখতে পাবেন—।’
রোশনের মনে হল, এরকম একটা জিনিস না দেখলে ও মিস করবে। তা ছাড়া ওর হাতে এখন অঢেল সময়। না, এখন বলতে শুধু আজ নয়—আগামী একশো বছর। কারণ, কারও সঙ্গে ওর কোনও সম্পর্ক নেই। কোনও পিছুটান নেই। কোনও দায়দায়িত্ব নেই।
প্রথম ওকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল ওর একমাত্র ছোটভাই কুশান। কী একটা আড়াইদিনের জ্বরে কুশান মারা গিয়েছিল। হাসপাতালের ডাক্তারবাবুরা কিছু ধরতেই পারেননি। সেখানে বেডে শুয়ে বারো-সাড়ে বারো বছরের রোগা ছেলেটা করুণ চোখে তাকিয়ে ছিল মায়ের দিকে, বাবার দিকে, আর ওর দাদার দিকে। বারবার জিগ্যেস করেছিল, ‘আমি কবে ভালো হব? কবে বাড়ি যাব?’
না, ওর আর বাড়ি ফেরা হয়নি।
তারপর এল বাবার পালা।
আর সবশেষে মা চলে গেল। তারপর…।
তারপর থেকে একা।
রোশন ছোট করে বলল, ‘ঠিক আছে, দেখি—।’ তারপর চা-বিস্কুটের দাম মিটিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল : ‘রাতে থাকার জন্যে একটা হোটেল বা গেস্টহাউসের নাম বলতে পারেন?’
‘কেন পারব না! আশাপুর লজ—চৌরাস্তার মোড়ের কাছে। স্বামী বিবেকানন্দের একটা পাথরের মূর্তি আছে—সাদা রঙের। সেখানে গেলেই আশাপুর লজ দেখতে পাবেন। এই রাস্তা ধরে দু-পা গেলেই রিকশো স্ট্যান্ড। রিকশো ধরে নিন—পনেরো টাকা ভাড়া নেবে। লজের মালিক বিশ্বরূপবাবু। লজে গিয়ে বিশ্ববাবুকে বলবেন, হাইরোডের চায়ের দোকান থেকে যোগেনদা পাঠিয়েছে…।’
‘ধন্যবাদ—’ বলে রোশন দোকানের বাইরে বেরিয়ে এল।
‘আশাপুর লজ’। চৌরাস্তা। বিবেকানন্দের মূর্তি।
তারপর কলাবতীর তীর। বিশ টাকার টিকিট। অদ্ভুত লড়াই।
রাস্তায় পা দিয়েই রোশন আকাশের দিকে তাকাল। চাঁদটা এখনও আগের মতোই বিউটিফুল।
রোশন যখন কলাবতীর তীরে এসে দাঁড়াল তখন বাঁকা চাঁদ আকাশে অনেকটা গড়িয়ে গেছে। রাতের অন্ধকার ডুবিয়ে দিয়েছে চারপাশ। তবে চাঁদ তার সান্ত ক্ষমতা নিয়ে অসম লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। আর খানিকটা দূরে বাঁশের ডগায় দুটো মলিন বালব জ্বলছে।
কলাবতীর তীরে এসে পৌঁছোনোমাত্রই বাতাসের উষ্ণতা হঠাৎ করে দু-ডিগ্রি কমে গেল। রোশন বুঝল ও নদীর খুব কাছে এসে গেছে।
কলাবতী খুব বড় নদী নয়, আর তাতে জলও তেমন নেই। ডানদিকে পাড়ের অনেকটা কাদা পেরিয়ে খেয়াঘাটে পৌঁছোতে হয়। সেই কাদায় নানানজনের পায়ের চাপে তৈরি হওয়া গর্ত। ঘাটে ঢালু করে কাঠের তক্তা পাতা রয়েছে। তারপর নৌকো।
কাঠের তক্তার দুপাশে দুটো লম্বা-লম্বা বাঁশ কাদার মধ্যে পোঁতা রয়েছে। বাঁশ দুটো ‘ওয়াই’-এর বাহুর মতো দু-দিকে খানিকটা করে হেলে আছে। তাদের মাথায় দুটো বালব জ্বলছে। সেই আলোয় কাদার গর্তগুলোয় গভীর ছায়া তৈরি হয়েছে।
ঘাটে কোনও লোকজন নেই—এ সময়ে থাকার কথাও নয়। তবে একটা বড় গাছের আড়ালে তিনটে খালি নৌকো ঘাটে বাঁধা রয়েছে। ছায়া-ছায়া দু-তিনটে মানুষ তার ওপরে বসে রয়েছে, গল্প করছে। তাদের বিড়ি অথবা সিগারেটের আগুন স্পষ্ট চোখে পড়ছে।
বাঁ-দিকটায় তাকাল রোশন।
কতকগুলো ছোট-ছোট ঘর চোখে পড়ল। সেগুলোর জানলা অথবা দরজা দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে। ঘরগুলোর আশেপাশে এলোমেলো গাছপালা। সেখানে এতই অন্ধকার যে, গাছগুলোর মাথা ভালো করে দেখা যাচ্ছে না।
ঘরগুলোর পর অনেকটা ফাঁকা জায়গা। তার পর রয়েছে একটা বড় মাপের টিনের চালে ছাওয়া ঘর। দেখতে অনেকটা গোডাউনের মতো। তার দেওয়ালগুলো ইটের গাঁথনি। দেখে বোঝা যায়, বেশ পুরোনো কনস্ট্রাকশন। সেই দেওয়ালে অনেকটা ওপর দিকে সারি-সারি অনেকগুলো ছোটমাপের খুপরি জানলা। সেইসব জানলা দিয়ে আলো ঠিকরে আসছে। গোডাউনটার একপাশে দাঁড় করানো রয়েছে অনেকগুলো মোটরবাইক আর সাইকেল।
চায়ের দোকানের যোগেনদা ঠিক এইরকম একটা ঘরের কথাই যেন বলেছিলেন! আরও বলেছিলেন, বাইরে থেকে চিৎকার-চেঁচামেচি শোনা যায়। কিন্তু কই, কিছুই তো শোনা যাচ্ছে না!
রোশন অবাক হয়ে চারপাশটা দেখছিল। কী অদ্ভুত শান্ত পরিবেশ! কোথাও কোনও শব্দ নেই। এমনকী কলাবতী ছোট নদী হওয়ায় তার ছলাৎ-ছলাৎ শব্দও তেমনভাবে শোনা যাচ্ছে না।
এদিক-ওদিক তাকিয়ে কোনও মানুষজনও দেখতে পেল না ও।
কী করবে ভাবছে, এমন সময় একটা অদ্ভুত শব্দ শুনতে পেল। ‘হুঃ’, ‘হুঃ’ শব্দ করে কেউ যেন ডাকছে। কোনও মানুষ যদি ঠোঁট ছুঁচলো করে শব্দ ছুড়ে দেয় তা হলে অনেকটা এরকম আওয়াজ হতে পারে।
শব্দটা বোধহয় অনেকক্ষণ ধরেই হচ্ছিল, কিন্তু রোশন সেটা খেয়াল করেনি। আর খেয়াল করলেও সেটাকে প্যাঁচা কিংবা কোনও নিশাচর প্রাণীর ডাক বলে ভেবেছে।
এখন মনোযোগ দিয়ে ডাকটা কয়েকবার শোনার পর ওর মনে হল, এটা কোনও মানুষেরই আওয়াজ।
কিন্তু একটা মানুষ বারবার এরকম অদ্ভুত আওয়াজ করবে কেন?
রোশন তাড়াতাড়ি পা চালাল সেই টিনের চালার দিকে।
যতই ও এগোতে লাগল, ‘হুঃ’, ‘হুঃ’ ডাকটা ততই জোরালো হতে লাগল।
একটু পরেই ও গোডাউনটার দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। দরজায় দুটো পাল্লা—কাঠের ফ্রেমে করোগেটেড টিনের শিট লাগিয়ে তৈরি। পাল্লা দুটো ভেজানো, তবে পাল্লার টিনের চাদরে জায়গায়-জায়গায় ফুটো।
একটা পাল্লা আস্তে করে ঠেলতেই খানিকটা খুলে গেল। সেই ফাঁক দিয়ে চৌকো চোয়াল, বড়সড় থ্যাবড়া মুখ, কালো মতন একটা লোক উঁকি মারল। রোশন পকেট থেকে দুটো দশ টাকার নোট বের করে লোকটার হাতে দিল। লোকটা টাকাটা নিয়েই রোশনকে হাত ধরে টেনে গোডাউনের ভেতরে ঢুকিয়ে নিল। ঠোঁটে আঙুল ছুঁইয়ে চুপ করে থাকার জন্য ইশারা করল। তারপর টিনের পাল্লা আবার ভেজিয়ে দিল।
ভেতরে তখন লড়াই চলছে।
যোগেনদা মোটেই মিথ্যে বলেননি। সত্যি, লড়াইটা ভীষণ অদ্ভুত।
ঘরটায় অনেক লোকের ভিড়—সেইজন্যই ভ্যাপসা গরম আর কেমন একটা গন্ধ। বোধহয় ঘামের গন্ধ আর বিড়ি-সিগারেটের গন্ধ মিশে এই গন্ধটা তৈরি হয়েছে।
ঘরের মাথার ওপরে লোহার অ্যাঙ্গেল দিয়ে তৈরি ট্রাস। সেখান থেকে তিনটে সিলিংফ্যান লম্বা ডাউনরডের ডগায় ঝুলছে এবং কালিঝুলি মাখা ফ্যানগুলো সাধ্যমতো ঘুরছে। ওদের একটু-আধটু আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে।
ঘরে আলো বলতে তিনটে টিউব লাইট আর সিলিং থেকে ঝুলিয়ে দেওয়া তিনটে ন্যাংটো বালব। এই আলোয় লড়াইয়ের রিং-এ ভালোই আলো হয়েছে, তবে রিং ঘিরে থাকা দর্শকদের মধ্যে আলো এবং ছায়া ভাগাভাগি হয়ে গেছে। আর ঘরের দেওয়াল পর্যন্ত সে-আলো পৌঁছোতে না পারলেও ছায়া অনায়াসে পৌঁছে গেছে।
গোডাউনের দু-দিকের দুই দেওয়ালে অনেক বস্তা থাকে-থাকে নানান উচ্চতায় লাট দিয়ে রাখা। বস্তার ভেতরে কী আছে কে জানে! দর্শকদের কেউ-কেউ লড়াইটা ঠিকঠাকভাবে দেখতে পাওয়ার জন্য বস্তার সেই লাটের ওপরে উঠে পড়েছে।
মোটামুটিভাবে গোডাউনের মধ্যিখানে, আলোর ঠিক নীচে, লড়াইয়ের রিং তৈরি করা হয়েছে। ইট গেঁথে যেমন পাঁচিল তোলা হয় ঠিক সেই ঢঙে বস্তার ওপরে বস্তা চাপিয়ে খাটো পাঁচিল তৈরি করা হয়েছে। সেই পাঁচিল দিয়ে গোলমতন একটা জায়গা ঘেরা। তবে পাঁচিলের এক জায়গায় ফুটদুয়েক ফাঁক রাখা হয়েছে—রিং-এর ভেতরে যাতায়াতের জন্য।
রোশন ভিড় ঠেলে রিং-এর খানিকটা কাছাকাছি এগিয়ে গেল। চারপাশ থেকে নাকে আসছে ঘামের কটু গন্ধ।
রোশন তাকাল রিং-এর দিকে।
রিং-এর মধ্যে লড়াই চলছে। দুজন ফাইটার লড়ছে—কিন্তু সেখানে কোনও রেফারিকে চোখে পড়ল না।
ফাইটার দুজনের স্বাস্থ্য মোটামুটি। পরনে বারমুডা ধরনের শর্টস। একজনের শর্টসের রং কালো, আর-একজনের বাদামি। ব্যস, পোশাক বলতে শুধু ওইটুকুই।
না, ভুল হল। কারণ, পোশাক বলতে আরও একটু কিছু আছে। সেটা হল, দুজন ফাইটারেরই চোখ কালো কাপড় দিয়ে বাঁধা। এবং সেই ‘অন্ধ’ অবস্থাতেই তারা লড়ছে।
রোশন অবাক হয়ে লড়াকু মানুষ দুজনের দিকে তাকিয়ে রইল। এরকম অদ্ভুত লড়াই দেখা তো দূরের কথা, ও কখনও শোনেওনি।
‘হুঃ’, ‘হুঃ’ জিগির চলছিল। একবারও থামেনি। কিছুক্ষণ লড়াইটা দেখার পর রোশন তার মানে বুঝতে পারল এবং সেইসঙ্গে লড়াইয়ের নিয়মটাও।
কালো প্যান্ট পরা ফাইটার তখন ‘হুঃ’, ‘হুঃ’ করে আওয়াজ করছিল আর রিং-এর মধ্যে চঞ্চল প্রজাপতির মতো নেচে বেড়াচ্ছিল। কখনও-কখনও বস্তার পাঁচিলে ধাক্কা খাচ্ছিল। আর বাদামি প্যান্ট পরা ফাইটার কোনও শব্দ করছিল না, বরং সেই ‘হুঃ’, ‘হুঃ’ শব্দ শুনে শব্দভেদী বাণের মতো প্রতিদ্বন্দ্বীকে তাড়া করে নাগালে পাওয়ার চেষ্টা করছিল।
রোশন বুঝতে পারল, একজন ফাইটার ওই অদ্ভুত আওয়াজ করে শত্রু ফাইটারকে নিজের পজিশন জানিয়ে দিচ্ছে, বলতে গেলে শত্রুকে ইনভাইট করছে। আর সেই ‘আবাহনী মন্ত্র’ যাতে ঠিকঠাক শোনা যায় সেইজন্য দর্শকরা নিঃশব্দে চুপটি করে দাঁড়িয়ে লড়াই দেখার উত্তেজনা ব্লটিং পেপারের মতো শুষে নিচ্ছে। তাদের কারও-কারও হাতে বিড়ি অথবা সিগারেট।
দুই ‘অন্ধ’ ফাইটারের অদ্ভুত কানামাছি লড়াই দেখতে লাগল রোশন।
একজন ফাইটার যখন ‘হুঃ’, ‘হুঃ’ চিৎকার করা অন্য ফাইটারকে নাগালে পেয়ে যাচ্ছে তখন সে পাগলের মতো ঘুষি-লাথি চালাচ্ছে, আর অন্যজন সেই মার থেকে পালিয়ে বাঁচার চেষ্টা করছে—কিন্তু কোনওরকম পালটা আক্রমণ করছে না। এবং সেই সময়টুকু ‘হুঃ’, ‘হুঃ’ চিৎকারটা বন্ধ থাকছে।
মার খাওয়া ফাইটার যখন আক্রমণকারী ফাইটারের কবজা থেকে ছিটকে বেরিয়ে যাচ্ছে তখনই শুরু হচ্ছে উলটপুরাণ। অর্থাৎ, যে এতক্ষণ মার দিচ্ছিল সে এবার ‘হুঃ’, ‘হুঃ’ আওয়াজ শুরু করে দিল। কারণ, এখন তার মার খাওয়ার পালা।
একজন লম্বা-চওড়া পেটানো চেহারার লোক রিং থেকে বেরোনোর পথের মুখটায় দাঁড়িয়ে ছিল। ফাইটাররা নিয়মে কোনও ভুলচুক করলেই সে চিৎকার করে সাবধান করছিল এবং কী করতে হবে নির্দেশও দিচ্ছিল। এই লোকটাই বোধহয় রেফারি। কালো হাফপ্যান্ট পরা ফাইটারকে সে ‘ওয়ান’ বলে ডাকছিল, আর বাদামি হাফপ্যান্টকে ‘টু’। বোধহয় লড়াইয়ের আগেই এইরকম নামের কথা ফাইটারদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।
এই মুহূর্তে কালো প্যান্ট বাদামিকে হাতের নাগালে পেয়ে গেছে এবং আন্দাজে ভর করে তার মাথা লক্ষ্য করে একটা ঘুসি চালিয়ে দিয়েছে।
ঘুসিটা লাগল বাদামির কানের এলাকায়। বাদামি ‘উঃ’ শব্দ করে বস্তার পাঁচিলের ওপরে টলে পড়ে গেল। ওপরের থাকের বস্তাটা পড়ে গেল রিং-এর বাইরে। জনগণ চাপা চিৎকার করে উঠল।
কালো তখন এলোপাতাড়ি লাথি চালাতে লাগল। খুঁজতে লাগল বাদামির শরীর। প্রথম দুটো লাথি শূন্যে খরচ হলেও পরের তিন-চারটে টার্গেটে লাগল। বাদামি পড়ে গেল মেঝেতে। যন্ত্রণায় কাতরে উঠল। সেই আওয়াজ শুনে কালো ঝুঁকে পড়ল। আরও কয়েকটা শব্দভেদী আঘাত ধেয়ে গেল বাদামিকে লক্ষ করে। একটা, দুটো, তিনটে, চারটে,…আরও…আরও…।
বাদামি তখন রক্তে মাখামাখি হয়ে গেছে। ওর চোখ বাঁধা কালো কাপড়টা ঘাম আর রক্তে ভিজে গেছে। ওর শরীরটা মেঝেতে পড়ে আছে—আর নড়াচড়া করছে না। তবে মুখ দিয়ে যন্ত্রণার টুকরো-টুকরো কাতরানির শব্দ বেরিয়ে আসছে। তাতেই বোঝা যাচ্ছে, বাদামি এখনও বেঁচে আছে।
রেফারি চট করে রিং-এর মধ্যে ঢুকে এল। কালো প্যান্টের চোখের পটিটা খুলে দিয়ে ওর একটা হাত শূন্যে তুলে ধরে চেঁচিয়ে বলল, ‘লড়াই খতম। এ-ম্যাচের উইনার ছবিয়া!’
এতক্ষণ ধরে চুপচাপ থাকা পাবলিক এবার হইহই করে চেঁচিয়ে উঠল।
বাদামি হাফপ্যান্ট তখন ধীরে-ধীরে মেঝেতে উঠে বসেছে। রেফারির ইশারায় দুটো ছেলে রিং-এ ঢুকে পড়ল। ওদের একজনের হাতে অনেকগুলো পাঁচশো আর একশো টাকার নোট। টাকাটা সে রেফারির হাতে দিল।
সেখান থেকে কিছু টাকা গুনে নিল রেফারি। তারপর সেটা ছবিয়ার হাতে দিয়ে বলল, ‘এই লড়াইয়ে ছবিয়া জিতেছে। তাই ও পাচ্ছে উইনারের প্রাইজ আড়াই হাজার টাকা…।’
পাবলিক আবার হইহই করে উঠল।
রেফারি এবার ‘সাবাস, ছবিয়া!’ বলে ছবিয়ার পিঠ চাপড়ে দিল। তারপর ছবিয়ার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করল।
হ্যান্ডশেক করার সময় ছবিয়ার মুখের ভাবটা এমন হল যেন ও কৃতার্থ হয়ে গেছে।
রোশনের মনে হল, রেফারি লোকটা বোধহয় একজন কেউকেটা হবে।
রেফারির বয়েস বত্রিশ-তেত্রিশ গোছের হবে। গায়ে একটা কালো হাফ শার্ট। স্বাস্থ্যের জন্য শার্টটা টান-টান হয়ে রয়েছে, নানান পেশির খবর জানিয়ে দিচ্ছে। মাথায় কোঁকড়ানো চুল—ছোট-ছোট করে ছাঁটা। গায়ের রং ময়লা। কপালটা বেশ চওড়া। তার তুলনায় চোখ সরু। কিছুটা থ্যাবড়া নাক, চৌকো চোয়াল। চওড়া গোঁফ। ডানকানে একটা সোনার মাকড়ি। ডানহাতের কবজিতে স্টিলের বালা, আর আঙুলে পাথর বসানো তিনটে আংটি।
লোকটার পায়ে আধময়লা জিনস আর ব্যবহারে কাহিল হয়ে যাওয়া কালো স্নিকার।
রিং-এ ঢুকে যাওয়া ছেলে দুটো তখন হেরে যাওয়া ফাইটারকে ধরে তুলছে, দাঁড় করাচ্ছে। সে দাঁড়ানোর পর তার চোখে বাঁধা কালো কাপড়টা ওরা খুলে দিল।
বাদামি প্যান্ট একটু খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে রেফারির কাছে এল।
রেফারি তার একটা হাত তুলে ধরে আগেরই মতোই চেঁচিয়ে বলল, ‘সুরেশের জন্য এবার হাততালি। এই ম্যাচে সুরেশ সেকেন্ড হয়েছে। ওর জন্যে সেকেন্ড প্রাইজ সাড়ে সাতশো টাকা। হাততালি দিন সব্বাই—।’
হাততালির আওয়াজে গোডাউন গমগম করে উঠল।
ফাইটার দুজন রিং থেকে বেরিয়ে গেল। রোশন দেখল, সুরেশ তো ভালোই আহত হয়েছে, তবে ছবিয়া যে আঁচড়হীন তা নয়। ওরও ঠোঁটের কোণে, বাঁ-ভুরুর ওপরে রক্ত জমে আছে।
রেফারি বলল, ‘আপনারা সবাই ওয়েট করুন। পনেরো-বিশ মিনিটের মধ্যেই পরের ফাইট চালু হয়ে যাচ্ছে। ফাইটারদের এখনই আমি রিং-এ ডেকে নিয়ে আসছি। ওরা এখানে এসে রাউন্ড দেবে। আপনারা ওদের হেলথ-ফেলথ দেখুন, সবকিছু ছানবিন করুন—তারপর বুকির কাছে বাজির পয়সা লাগান…।’
রেফারির কথা শেষ হতে-না-হতেই নতুন দুজন ফাইটার রিং-এর ভেতরে এসে হাজির। রেফারি ওদের নিয়ে রিং-এর মধ্যে রাউন্ড মারতে লাগল আর বলতে লাগল, ‘নিন, ভাইসব—বাজি লাগান। বুকি ওই কর্নারে টেবিল নিয়ে বসে আছে—’ হাত তুলে গো-ডাউনের একটা কোণের দিকে দেখাল রেফারি : ‘আপনারা ওখানে গিয়ে বাজির পয়সা লাগান…।’
দর্শকদের মধ্যে হুড়োহুড়ি শুরু হয়ে গেল।
রোশন বেশ অবাক চোখে চারপাশটা দেখছিল। মনে হচ্ছিল, ও একটা নতুন জগতে ঢুকে পড়েছে। ও ভিড় ঠেলেঠুলে বুকির টেবিলের দিকে এগোচ্ছিল। না, ওর বাজি ধরার কোনও মতলব ছিল না। শুধু ব্যাপারটা দেখার জন্য কৌতূহল হচ্ছিল।
বেশ কিছুক্ষণের ধাক্কাধাক্কি পার করে শেষ পর্যন্ত ও বুকির টেবিলের কাছে পৌঁছোল।
সেখানে দেওয়াল ঘেঁষে রাখা একটা ছোট কাঠের টেবিল আর দুটো প্লাস্টিকের চেয়ার। চেয়ারে বসে আছে একজন রোগাপটকা মাঝবয়েসি লোক আর একজন পঁচিশ-ছাব্বিশের ছোকরা।
মাঝবয়েসি লোকটির চোখে চশমা, মাথায় একটা রঙিন রুমাল বাঁধা, আর গালে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। পরনে একটা ঢোলা হাফ শার্ট আর ময়লা পায়জামা। পায়ে হাওয়াই চপ্পল। থেকে-থেকেই সে নাক টানছে আর হাতের পিঠ দিয়ে নাক মুছছে। এবং সেই নাক মোছার চকচকে রেশ থেকে যাচ্ছে গালের ওপরে।
মাঝবয়েসি লোকটির পাশে বসা পঁচিশ-ছাব্বিশের ছেলেটির চেহারাও রোগার দিকেই। গায়ের রং মাঝারি। মাথায় অনেক চুল। পরনে সাধারণ শার্ট-প্যান্ট আর চপ্পল।
ওরা দুজনেই ভীষণ ব্যস্ত।
মাঝবয়েসি লোকটি সবাইকে আগের লড়াইয়ের বাজির পেমেন্ট দিচ্ছে। পেমেন্ট দেওয়ার আগে বাজি ধরার চিরকুটটা নিয়ে চেক করে দিচ্ছে পঁচিশ-ছাব্বিশের ছেলেটি। এরই ফাঁকে-ফাঁকে নতুন লড়াইয়ের বাজির টাকাও নিচ্ছে ওরা। সেই টাকা নিচ্ছে ছেলেটি, আর চিরকুট ইস্যু করছে রোগাপটকা মাঝবয়েসি মানুষটা।
ওদের দুজনকে ঘিরে যথেষ্ট ভিড়। সেই ভিড় থেকে সামনে বাড়ানো রয়েছে অসংখ্য হাত। দেখে মনে হচ্ছে, দুর্ভিক্ষ হয়েছে এমন একটা অঞ্চলে ওরা দুজন খাবার বিলি করতে এসেছে। আর, খেতে না পাওয়া হতভাগ্য মানুষগুলো এককণা খাদ্যের আশায় ওদের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে দুই দেবদূতের দিকে।
রোশনের বুক ঠেলে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। সত্যি, এর চেয়ে সত্যিকারের দুর্ভিক্ষ হওয়াটা বোধহয় অনেক ভালো ছিল।
বুকি দুজনের চেয়ার-টেবিল থেকে চার-পাঁচ হাত দূরে দেওয়ালের গায়ে একটা ছোট জায়গা কাপড় টাঙিয়ে ঘেরা রয়েছে—অনেকটা যেন গ্রাম-গঞ্জের নাটকমঞ্চের পাশে তৈরি গ্রিনরুম।
কৌতূহলে সেদিকটায় এগিয়ে গেল রোশন।
সেখানে বেশ কিছু লোকের জটলা। সেটা পেরিয়ে নজর চালাতেই গ্রিনরুমের ভেতরের দৃশ্যটা নজরে পড়ল।
সেখানে মাঝারি আলোর একটা বালব জ্বলছে। একটু আগেই যারা লড়াই শেষ করল সেই ফাইটার দুজন দুটো টুলের ওপরে বসে আছে। তাদের সেবা-শুশ্রূষা চলছে। একটা বছর তেরো-চোদ্দোর ছেলে একটা ছোট্ট টিনের বাক্স হাতে ওদের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে। বাক্সটার ডালায় লাল রঙের আঁকা একটা ‘প্লাস’ চিহ্ন—তবে তার রং এ-জায়গায় সে-জায়গায় চটে গেছে।
ছেলেটার পাশেই একজন লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার ডানহাতে ওষুধে ভেজানো তুলো। সে বারবার ঝুঁকে পড়ে সুরেশ নামের ফাইটারের বাঁ-ভুরুতে আর ঠোঁটের ডানদিকে সেই তুলোর পোঁটলাটা চেপে-চেপে ধরছে।
গ্রিনরুমের ডানদিক ঘেঁষে পাতা রয়েছে একটা লম্বা বেঞ্চ। সেই বেঞ্চে চারজন যুবক পাশাপাশি বসে রয়েছে—ঠিক যেন স্কুলের বেঞ্চে বসা ছাত্র। তিনজনের বয়েস ছাব্বিশ থেকে আটাশের মধ্যে, আর একজনের বয়েস সাঁইত্রিশ কী আটত্রিশ হবে। তাই চারজনের মধ্যে বেশি বয়েসের লোকটিকে ‘অড ম্যান আউট’ বলে মনে হচ্ছে। তার মাথায় এক-দু-গাছা পাকাচুলও চোখে পড়ছে।
রোশন ভাবছিল, এই চারজন এভাবে বেঞ্চে চুপচাপ বসে আছে কেন?
এপাশ-ওপাশ তাকিয়ে ও এই প্রশ্নের উত্তরটা খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু পেল না। তারপর যখন ও ভাবছে, কাউকে ব্যাপারটা জিগ্যেস করলে হয়, ঠিক তখনই ওর একেবারে গা ঘেঁষে দাঁড়ানো একটা লোক বলে উঠল, ‘ওরা সব ফাইটার—পরপর জোড়ায়-জোড়ায় লড়বে…।’
রোশন লোকটার দিকে তাকাল।
বয়েস পঁয়তাল্লিশ কী তার একটু বেশিই হবে। ফরসা লম্বাটে মুখ। বড়-বড় চোখ। চোখে চশমা। ছোট মাপের চাপা নাক। সারা মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি-গোঁফ।
সবমিলিয়ে মুখটায় কেমন যেন একটা কমিক ভাব রয়েছে—অনেকটা সার্কাসের জোকারের পেইন্ট করা মুখের মতন।
লোকটা একটু কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। হাতে জ্বলন্ত বিড়ি—তাতে ঘন-ঘন টান দিচ্ছে। তা ছাড়া মুখ থেকে নেশার গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।
‘আশাপুরে নতুন বুঝি?’ চোখ নাচিয়ে প্রশ্ন করল লোকটা।
‘হ্যাঁ—আজই এসেছি…।’ সায় দিয়ে মাথা নাড়ল রোশন।
‘আমি এখানকার…লোকাল…সেই জম্মো থেকেই…।’
রোশন একটু হাসল—কোনও কথা বলল না।
‘আমার নাম নিত্যানন্দ—সবাই নিতুয়া বলে ডাকে। নিত্যানন্দ থেকে নিতু…তারপর নিতু থেকে নিতুয়া…।’ বিড়িতে টান দিল দুবার। থু-থু করে কিছু একটা মুখ থেকে ছিটকে দিল : ‘তোমার নাম কী?’
‘রোশন—।’ লোকটার সঙ্গে কথা বলতে রোশনের কেমন যেন অ্যালার্জি হচ্ছিল।
‘বাঃ! রোশন—রোশনাই। বাপের ঘর আলো করা লালটু ছেলে…।’ নিতু হাসল হ্যা-হ্যা করে।
রোশনের হাসিটা ভালো লাগল না। ওর কুশানের কথা মনে পড়ে গেল। ও ছিল ঘর আলো করা ছেলে। কী দারুণ ছিল লেখাপড়ায়। আর দেখতেও ছিল কী ফুটফুটে!
এইচ. এস.-এর পর রোশনের আর লেখাপড়া হয়নি। হয়নি মানে পড়তে ইচ্ছে করেনি আর। ড্রাইভিং শিখে লাইসেন্স বের করেছিল। কয়েক বছর এর-তার ট্যাক্সি আর প্রাইভেট কার চালিয়েছিল। এইচ. এস. পাশ করার পরপরই তো গন্ডগোল হল। একটা নিষ্ঠুর ঝড় ওদের ফ্যামিলিটাকে ওলটপালট করে দিল। এই নিতু লোকটা তার কতটুকু জানে!
নাঃ, নিতুর কোনও দোষ নেই।
‘তা আসছ কোত্থেকে?’
‘কলকাতা থেকে—।’
‘আমাদের এখানে কি কাজ নিয়ে এসেছ?’
‘না, সেরকম কোনও কাজ নিয়ে আসিনি।’
‘আছ কোথায়?’
‘ ”আশাপুর লজ”-এ উঠেছি। রেট বেশ সস্তা…।’
‘হুঁ—।’
রোশন ওকে জিগ্যেস করল, ‘এই লড়াইয়ের ব্যবস্থাটা কারা করে?’
নিতু রোশনের জামা ধরে একপাশে টেনে নিল। রোশন লক্ষ করল, ও সামান্য পা টেনে চলছে। একটু ফাঁকা জায়গায় গিয়ে নিতু চাপা গলায় বলল, ‘বলছি—তবে কারও সঙ্গে গজল্লা কোরো না। এই ফাইটের শো চালায় পলান—ওই যে, যে-লোকটা লড়াইয়ের রেফারি হয়। ওর সঙ্গে আরও আমচা-চামচা আছে…।’
রেফারির থ্যাবড়া নাক, চৌকো চোয়াল মুখটা রোশনের চোখের সামনে ভেসে উঠল।
‘এই ফাইট শো থেকে পলানরা হেভি পাত্তি ইনকাম করে। প্রত্যেক শনিবার এই গোডাউনে লড়াই হয়…রাত আটটা থেকে—।’
‘পুলিশ বা আর-কেউ কিছু বলে না।’
‘পুলিশ?’ খিকখিক করে হাসতে লাগল নিতু। হাসি থামলে পর গলা সাফ করল। শেষ হয়ে যাওয়া বিড়ির টুকরোটা মাটিতে ফেলে চপ্পল দিয়ে ঘষে দিল। তারপর বলল, ‘পুলিশ হচ্ছে কোলের খোকা। ন্যাংটো, কথা বলতে পারে না, কারও কথা বুঝতেও পারে না। মানে, লজ্জা কাকে বলে জানে না। সেইসঙ্গে বোবা আর কালা। শুধু নিজের খিদেটুকু বোঝে। আর ওদের খিদের মানে তো বোঝো! তো পলান সে-খিদে রেগুলার মিটিয়ে দেয়।
‘তা ছাড়া, এ-খেলা বন্ধ করবে কেন? এ-খেলা চললে তো সবার লাভ। অবশ্য ভুলভাল ফাইটারের ওপরে বাজি ধরে ফেললে লোকসান হতে পারে। পলান লোকটা শয়তান হলেও টাকা-পয়সা ছড়ায়। যেমন, ধরো না, যে-সে ওর এই ফাইটে নাম দিতে পারে। তো তার চেহারা রোগাপটকা হলেও। যদি সে ফাইটে হেরে যায় তা হলেও সে কমবেশি টাকা পাবে। গরিব লোকজন অনেক সময় এ-লড়াইয়ে নাম দেয় শুধুমাত্র দু-চারটে টাকার জন্যে। তা ছাড়া চোখ বেঁধে লড়াই হয় বলে কোনও ফাইটারই তেমন চোট-ফোট পায় না। তা হলে এ লড়াই মন্দ কী!’
রোশন বলল, ‘বুঝেছি।’ তারপর কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকার পর জিগ্যেস করল, ‘বেঞ্চে যে-চারজন ফাইটার বসে আছে তার মধ্যে তো একজনের বয়েস একটু বেশি মনে হচ্ছে। ওই যে, বেঞ্চের একেবারে এ-সাইডে বসে আছে…।’ গলা উঁচু করে গ্রিনরুমের বেঞ্চের দিকে দেখাল রোশন।
নিতু ঠোঁট চওড়া করে হাসির ভঙ্গি করল। চশমাটা নাড়াচাড়া দিয়ে ঠিক করল। তারপর বলল, ‘হুঁঃ! ও হচ্ছে গনিরাম। গনি বহুবার এখানকার ফাইটে নাম দিয়েছে। কখনও জিতেছে, কখনও মুখ থুবড়ে পড়েছে। আসলে ও নাম দেয় অভাবে। আশাপুরের সুতোকলে কাজ করত। কীসব চুরিচামারি করেছে বলে চাকরি গেছে। সে প্রায় বছরখানেক হল। তারপর থেকে ছন্নছাড়া হয়ে গেছে।’
রোশন একটু অবাক হল। ছন্নছাড়া। ওর মতন! যার তিনকূলে আর কেউ নেই! আত্মীয়স্বজন বলতে আকাশ, বাতাস, মাটি, গাছপালা আর নদী-নালা। ওরাই এখন রোশনকে ঘিরে থাকে, ছুঁয়ে থাকে।
‘গনিরামের কোনও ফ্যামিলি নেই?’ গনিরামের ব্যাপারে কৌতূহল হল রোশনের।
‘না, আছে—’ জিভ দিয়ে একটা বিচিত্র শব্দ করে বলল নিতু। তারপর আঙুল তুলে গ্রিনরুমের দিকে দেখাল : ‘ওই যে…ওটা গনিরামের ছেলে…।’
আঙুলের নিশানা লক্ষ্য করে তাকাল রোশন! গনিরামের কাছে একটা দশ-বারো বছরের ছেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ছেলেটার গায়ে নীল রঙের একটা টি-শার্ট, পায়ে কালো হাফপ্যান্ট। একহাতে একটা বড় পলিথিনের প্যাকেট, আর অন্যহাতে একটা ললিপপ।
ছেলেটা ওর বাবার সঙ্গে কীসব কথা বলছে, আর তার ফাঁকে-ফাঁকে ললিপপে একদফা ‘চকাৎ’ করছে। রেফারি তখন চেঁচিয়ে পরের লড়াইয়ের ফাইটারদের নাম ঘোষণা করছে। তার মধ্যে গনিরামের নাম রয়েছে। এবং তার অপোনেন্ট ফাইটার কামাল।
রেফারি আরও বলছে, আর পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যেই নেক্সট ফাইট শুরু হবে। নিতুয়া নীচু গলায় রোশনকে গনিরামের কথা বলছিল।
গনিরাম আশাপুরের ‘মহামায়া কটন মিল’-এ চাকরি করত। বছর চারেক আগে ওর বউ আরতি আশাপুর হাইরোডে ট্রাক চাপা পড়ে মারা যায়। আরতি কলকাতা থেকে ফিরছিল। তখন সন্ধে হয়-হয়। বাস থেকে নেমে রাস্তা পার হওয়ার সময় একটা ফুল পাঞ্জাব ট্রাক ওকে চটকে দেয়। সে-দৃশ্য চোখে দেখা যায় না।
গনিরাম অ্যাক্সিডেন্টের খবরটা পেয়ে একেবারে পাগল হয়ে গিয়েছিল। ওর ছেলে ববিনের বয়েস তখন কত? খুব বেশি হলে সাত কি আট বছর। ওই একটাই ছেলে ওর।
বউয়ের শোক কাটিয়ে উঠতে গনিরামের এক-দেড়বছর লেগেছিল। ওর এক বিধবা দিদি ওর সঙ্গে থাকে—সাবিত্রী। তো সাবিত্রী ববিনের দেখভাল করতে লাগল। তার সঙ্গে রান্নাবান্না সব। কিন্তু বাচ্চাটা বাপের খুব নেওটা। সবসময় বাপের সঙ্গে থাকতে চায়, বায়না করে। বাবা রোজ সুতোকলের কাজে রওনা দিলে ববিন হাত-পা ছোড়ে, চেল্লামেল্লি করে। এই নিয়ে রোজ লাফড়া। তাকে সাবিত্রী অনেক কষ্টে মন-টন ভুলিয়ে সামলেসুমলে ঠান্ডা করে। তো এসব করতে-করতে স্কুল কামাই হয়। ব্যস!
শেষ পর্যন্ত বাচ্চাটা স্কুল ছেড়ে দিল। গনিরাম ওকে এতটাই ভালোবাসে যে, তেমন বকাঝকা করে শাসন করে ওকে আর স্কুলে পাঠাতে পারল না।
‘আপনি এত কথা জানলেন কেমন করে?’ রোশন জিগ্যেস করল।
‘জানব না!’ হাসল নিতু : ‘আমি আর গনিরাম তো একই বস্তিতে থাকি। ওটাকে সবাই বারো নম্বর বলে। ওই তো, রেল-লাইনের ধারে…।’
‘গনিরামের চাকরিটা গেল কেমন করে?’
‘ওই যে বললাম, চুরিচামারি করে…।’
‘কী চুরি করেছে ও?’ রোশন গনিরামকে দেখছিল। লোকটা বেঞ্চ ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। ছেলেকে জড়িয়ে ধরে আদর করছে, মাথায় হাত বোলাচ্ছে।
‘কী চুরি করেছে সেটা ঠিকঠাক জানি না, তবে এর-তার মুখে শুনেছি, মিল থেকে সুতোর লাছি হড়কে বাইরে কোন এক গেঞ্জি কোম্পানির কাছে বেচতে চেষ্টা করেছিল। কেসটা কীভাবে যেন ক্যাচাল হয়ে যায়।’ একটা বড় মাপের শ্বাস ফেলল নিতুয়া। তারপর : ‘ব্যস! চাকরিতে হাত ধুয়ে বসল…।’
‘তারপর?’
‘তারপর আর কী! অভাব পাগলা কুত্তার মতো কামড়ে ধরল। একটা কাজ জোটানোর জন্য আর পাঁচটা কলকারখানায় অনেক ঘোরাঘুরি ছুটোছুটি করল, কিন্তু পোড়া কপাল! কিছুই জোটাতে পারল না। তখন নেশা-টেশা ধরল…আর তার সঙ্গে এই ব্লাইন্ড ফাইট। যদি ফাইটে জিততে পারে তা হলে জম্পেশ পয়সা। আর যদি হেরে যায় তা হলেও কম-বেশি কিছু জোটে…।’
রোশন গনিরামের ছেলেকে অবাক হয়ে দেখছিল। গোডাউনের এই ব্লাইন্ড ফাইটের আসরে ববিন ছাড়া আর কোনও ছোট ছেলে নেই।
ও নিতুকে জিগ্যেস করল, ‘নিতুদা, এখানে ববিন ছাড়া আর তো কোনও ছোট ছেলে-টেলে দেখছি না। তা হলে এই বাচ্চাটাকে ঢুকতে দিয়েছে কেন?’
‘নিতুদা! তুমি আমাকে দাদা বললে! আমাকে দাদার সম্মান দিলে!’ রোশনের বাঁ-হাতটা খামচে ধরল নিতু। কেমন যেন ধরা গলায় বলল, ‘আমাকে সবসময় সবাই দুরছাই করে। পোকামাকড় কি জঞ্জাল ভাবে। না, ভাই রোশন, তুমি একজন স্পেশাল ভদ্দরলোক। তোমার ভালো হবে। কলকাতার লোক বলে তোমার কোনও গুমোর নেই…।’ নিতু রোশনকে টেনে আরও একটু ফাঁকা জায়গায় নিয়ে গেল। তারপর বলল, ‘ববিন ছেলেটা বাপ ছাড়া কিছু বোঝে না। সবসময় বাবার লেজ ধরে থাকে। তাই গনিরাম লড়তে এলে পলানরা ওর ছেলেকে অ্যালাউ করে—তবে ববিনকে ফাইট দেখতে দেয় না। এক সাইডে বাচ্চাটাকে বসিয়ে রাখে…। ওই যে, দ্যাখো, কানুয়া ববিনকে হাত ধরে সাইডে নিয়ে যাচ্ছে। এবার তো গনিরামের ফাইট—।’
‘কানুয়া কে?’
‘পলানের ডানহাত, মানে, পলানের অনেকগুলো ডানহাত—তার মধ্যে একটা।’ চোখের একটা ভঙ্গি করে হেসে উঠল নিতু। তারপর : ‘পলান হচ্ছে মা দুর্গার কাছাকাছি। ওর অনেকগুলো ডানহাত, অনেকগুলো বাঁ-হাত। আশাপুরে ক’দিন যদি থেকে যাও তা হলে সব টের পেয়ে যাবে।’
আশাপুরে রোশন ক’দিন থাকবে সেটা আশাপুরই জানে! ইচ্ছে আছে কাল সকালে জগন্ময়ীর কালীমন্দির দেখতে যাবে। তারপর আশাপুরের এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়াবে। মানুষজন দেখবে, অনুভব করবে। তারপর বল গড়াতে-গড়াতে যেদিক পানে যায়।
‘লড়াই শুরু হচ্ছে—’ পলান চিৎকার করে বলল, ‘সবাই চুপ এবার!’
ভিড়ের পাঁচিলের জন্য পলানকে রোশন দেখতে পাচ্ছে না, তবে ওর হুকুমদারি ফরমান শুনতে কোনও অসুবিধে হল না। পলানের কথা বলার ঢং থেকে যেন তেজ ছিটকে বেরোচ্ছিল। তার সঙ্গে মিশে ছিল প্রত্যয়।
পলানের হুকুম শোনামাত্র সবাই চুপ করে গিয়েছিল। এবং ফাইটারদের ‘হুঃ’, ‘হুঃ’ ডাক শোনা গেল।
লড়াই শুরু হয়ে গেছে।
রোশন নিতুর হাত ছাড়িয়ে ভিড়ের পাঁচিলের কাছে এগিয়ে গেল। নিতুকে বলল, ‘নিতুদা, লড়াইটা একটু দেখব। আপনিও আসুন না, দেখবেন। গনিরাম তো আপনার পাড়ার লোক!’
নিতুয়া দু-একসেকেন্ড কী ভেবে রিং-এর দিকে এগোল। দু-একজন দর্শককে ঠেলে সরিয়ে জায়গা তৈরি করে ভিড় ভেদ করতে লাগল। বিড়বিড় করে বলল, ‘এসব লড়াইয়ে নাম লিখিয়ে ফাটকা খেলার কী দরকার!’
রোশন নিতুয়ার প্রায় পাশেই ছিল। নিতুর কথার উত্তরে কী একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই পিছন থেকে কেউ ওর কাঁধে টোকা দিল।
পিছন ফিরে তাকাল রোশন।
রোগা টিংটিঙে চেহারার কালো রঙের বেঁটে মতন একটা ছেলে চোখে প্রশ্ন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সাদা ফুলশার্ট, সাদা প্যান্ট। এই গুমোট আবহাওয়ায় ফুলশার্ট কী করে গায়ে দিয়ে আছে কে জানে!
‘এরিয়ায় নিউ নাকি?’ নীচু গলায় প্রশ্ন করল ছেলেটা। কারণ, লড়াই চলছে।
প্রশ্নটা বুঝতে দু-এক সেকেন্ড সময় লাগল রোশনের। একটু বিরক্তভাবে ভুরু কুঁচকে ও আলতো গলায় জবাব দিল, ‘হ্যাঁ—কেন?’
ছেলেটা চোখ বড় করে অবাক হয়ে তাকাল। ব্যঙ্গ করে বলল, ‘বাব্বা! কোশ্চেনের উত্তরে কোশ্চেন? আপনি মাস্টারমশাই নাকি?’
রোশন কী জবাব দেবে বুঝে উঠতে পারছিল না।
ছেলেটা আবার জিগ্যেস করল, ‘নাম কী?’
‘রোশন—।’ নীচু গলায় বলল রোশন।
‘কবে আশাপুরে এসেছেন?’
‘আজই…।’
‘আপনি হোয়্যার স্টে করছেন, মাস্টারজি?’
রোশন এবার একটু রিয়্যাক্ট করতে যাচ্ছিল। সেটা ওর মুখের ভাব দেখে নিতুয়া বুঝতে পারল। তাই রোগা ছেলেটার চোখের আড়ালে রোশনের হাত টিপল। বলতে চাইল, ‘চেপে যাও—।’
রোশন নিজেকে সামলে নিল। ঠান্ডা গলায় বলল, ‘ ”আশাপুর লজ”-এ উঠেছি।’
‘ও, বিশ্বরূপ জোয়ারদারের হোটেলে…।’
কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর রোশন খুব শান্ত গলায় বলল, ‘কেন, কোনও প্রবলেম হয়েছে?’
‘না, প্রবলেম কিছু হয়নি—’ মুখের ভেতরে আঙুল ঢুকিয়ে দাঁতের কোণ থেকে কিছু একটা বের করার চেষ্টা করল ছেলেটা। তারপর : ‘যাতে প্রবলেম না হয় তার জন্যে আপনাকে একটু ছানবিন করছি। পলানদার এরিয়াতে এটাই স্ট্যান্ডার্ড সিস্টেম…।’
ও। এবারে ব্যাপারটা একটু পরিষ্কার হল রোশনের কাছে। এই রোগা ছেলেটা পলানের চ্যালা। আশাপুরের এই এলাকার খবরদারি করে।
ছেলেটা এবার নিতুয়ার দিকে তাকাল। নিতুয়া হঠাৎই ভয় পেয়ে কেমন যেন সিঁটিয়ে গেল।
তাচ্ছিল্যের গলায় ছেলেটা বলল, ‘কীরে পকেটমারের বাচ্চা! তুই এই জেন্টেলম্যান মাস্টারজির সঙ্গে কী ধান্দায় লেপটে আছিস? চিকেন বানাবি?’
নিতুয়া কোনও জবাব দিল না। রোশনের শরীরের আড়ালে যেন লুকোতে চেষ্টা করল।
ছেলেটা রোশনকে বলল, ‘কেয়ারফুল, মাস্টারজি! এই নিতু সালা হাতসাফাইয়ের সুপ্যারম্যান…।’ তারপর আঙুল দিয়ে দাঁত খোঁচাতে-খোঁচাতে চলে গেল।
রোশন নিতুকে জিগ্যেস করল, ‘নিতুদা, এই ছেলেটা কে? পলানের আর-একটা ডানহাত?’
নিতু ছেলেটার চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে ছিল। সেদিকে চোখ রেখেই বলল, ‘হ্যাঁ। ওর নাম কাটা নগেন। সালা রাম হারামি…।’
‘কাটা নগেন? হঠাৎ ”কাটা” কেন?’ রোশন জিগ্যেস করল। বখাটে ছেলেটা নিতুকে যে পকেটমার বলে অপমান করে গেল, সেটাও রোশনের ভালো লাগেনি।
রোশনের দিকে তাকাল নিতু। মাথার কাঁচাপাকা চুলে হাত বোলাল, যেন কাটা নগেনের ছুড়ে দেওয়া অপমানে ওর বড়-বড় চুলের ডিজাইন ঘেঁটে গেছে। তারপর চশমাটাকে নাড়াচাড়া দিয়ে ঠিকঠাক করে বসাল।
‘সাত-আট বছর আগে একদিন রাত্তিরবেলা রেল লাইনের ধারে বসে কাটা নগেন নেশা করছিল। তখন ও ওয়াগন ব্রেকারদের কবজায় পড়ে যায়। পুরোনো কোনও দুশমনি ছিল বোধহয়। তো ওদের দলের একজন চপার দিয়ে নগেনকে অ্যাটাক করে। নগেন ছুটে পালায় বটে, তবে ওর পিঠে চপারের দু-তিনটে কোপ পড়ে। বেশ কিছুদিন হাসপাতালে থাকার পর ও সেরে ওঠে—কিন্তু পিঠে ওই কাটা দাগগুলো থেকে যায়। তো সেই থেকে কাটা নগেন…।’
‘ও। এবার চলুন, রিং-এর কাছে চলুন…।’
লোকজনের ফাঁকফোকর দিয়ে ওরা রিং-এর দিকে এগিয়ে গেল।
ওই তো দেখা যাচ্ছে গনিরামকে! কালো কাপড় দিয়ে ওর চোখ বাঁধা। খালি গা, কোমরে কালো হাফপ্যান্ট। ওর কাছ থেকে হাতচারেক দূরে ওর ‘অন্ধ’ প্রতিদ্বন্দ্বী কামাল। ওরও খালি গা। তবে কোমরে বাদামি হাফপ্যান্ট। ঠোঁট ছুঁচলো করে ‘হুঃ’, ‘হুঃ’ আওয়াজ করছে।
দুজনের শরীরই ঘামে ভেজা।
গনিরামের বয়েস প্রতিদ্বন্দ্বী ফাইটারের চেয়ে বেশি, কিন্তু অভিজ্ঞতাও তো বেশি! তাই সবাইকে অবাক করে দিয়ে ও কামালের আওয়াজ লক্ষ্য করে হিংস্র পশুর মতো লাফ দিল। এবং তাকে নাগালে পেয়েও গেল।
ক্ষুধার্ত বাঘ যেভাবে ছুটন্ত হরিণের গলা কামড়ে ধরে তাকে আঁকড়ে ধরে, গনিরাম অনেকটা সেইভাবে কামালকে জাপটে ধরল। তারপর ওর পেটে একের পর এক ঘুসি চালাতে লাগল।
গনিরাম জানে যে, কামাল যদি ওর বাঁধন থেকে একবার ছিটকে যায় তা হলে গনিরামকে তখন ‘হুঃ’, ‘হুঃ’ চিৎকার করতে হবে, আর মার খাওয়ার জন্য তৈরি থাকতে হবে। তাই গনিরাম যেন মরিয়া। কামালকে জাপটে ধরে আন্দাজে ওর মাথা লক্ষ্য করে একের পর এক ঘুসি চালিয়ে যাচ্ছে।
কিন্তু কামালকে ধরে রাখতে বেশ কসরত করতে হচ্ছিল। কারণ, দুজনেরই ঘামে ভেজা শরীর। বারবার পিছলে যেতে চাইছে কামাল। কিন্তু তারই মধ্যে গনিরামের একটা মোক্ষম ঘুসি কামালের বাঁ-রগের ওপর গিয়ে পড়ল। এবং কামালের শরীরটা এলিয়ে গেল।
কিন্তু সেটা মাত্র কয়েক সেকেন্ডের জন্য। তারপরই এক ঝটকায় গনিরামের বাঁধন ছাড়িয়ে কামাল ছিটকে গেল। রিং-এর পাঁচিলের বস্তায় ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ল মেঝেতে। এবং সঙ্গে-সঙ্গে উঠে দাঁড়াল।
গনিরাম ততক্ষণে জিগির তোলা শুরু করে দিয়েছে। ও ভেবেছিল এ-দানেই ফাইটটা শেষ করে দেবে, কিন্তু সেটা আর হল না। লড়াইটা জিততে পারলেই আড়াই হাজার টাকা! যদিও ফাইটারের লেভেল বুঝে পলান রেট ঠিক করে। এই গোডাউন ফাইটে গনিরামের যা বডি আর ট্র্যাক রেকর্ড তাতে ও আড়াই হাজার টাকাই পাবে। পেলে মুদিখানা দোকানের ধার অনেকটা শোধ করা যাবে। পাঁচলিটার কেরোসিন কিনে স্টক করা যাবে। ছেলেটার একটা জামা, আর একটা প্যান্ট কেনা খুবই দরকার। কারণ, ও একটা জামা, একটা প্যান্ট দিয়ে কোনওরকমে চালাচ্ছে। সেগুলো আবার বেশ কয়েক জায়গায় ছিঁড়ে গেছে। যদিও দিদি সেলাই করে মোটামুটি জুড়ে দিয়েছে।
গনিরামকে খুঁজে পেয়েছে কামাল। এলোপাতাড়ি কিল, চড়, ঘুসি চালাচ্ছে।
কামালের ডানভুরুর পাশটায় ফেটে গেছে। জ্বালা টের পাচ্ছে ও। কী যেন একটা চোখের পাশ দিয়ে খুব ধীরে-ধীরে গড়িয়ে নেমে আসছে। জায়গাটা একটু সুড়সুড় করছে। হাত দিয়ে দেখতে ইচ্ছে করল কামালের। কিন্তু কী একটা ভয়ে ও জায়গাটা আন্দাজ করে হাত বাড়াল না। যদি চটচটে কোনও জিনিস হয় তা হলে কামালের মনের জোর কমে যেতেও পারে।
হঠাৎই গনিরামের একটা সুযোগ এসে গেল। ঘামের জন্য কামালের বাঁধন একটু নড়বড়ে হয়ে গিয়েছিল। এক জোরালো ঝটকা দিয়ে সেই বাঁধন ছিঁড়ে ফেলল গনিরাম। আন্দাজে ভর করে যতটা পারল দূরে সরে গেল।
কামালের গায়ে জোর কম নয়। ওর সঙ্গে সরাসরি লড়াইয়ে তিন রাউন্ড টিকে থাকা বেশ কঠিন। এই ব্লাইন্ড ফাইট গেমে এক-একটা রাউন্ড পাঁচমিনিটের। বেশিরভাগ লড়াই এখানে দু-রাউন্ডের মধ্যেই শেষ হয়ে যায়। একজন প্রতিযোগী পুরোপুরি কাহিল হয়ে পড়লে তবেই লড়াই শেষ হয়। নাঃ, গনিরামকে মাথা খাটিয়ে একটা কায়দা বের করতে হবে।
কামাল তখন জিগির তোলা শুরু করেছে। চোখে কাপড় বাঁধা থাকলেও কোনদিক থেকে আক্রমণ আসতে পারে সেটা আঁচ করার জন্য ও এপাশ-ওপাশ মাথা ঘোরাচ্ছে। দর্শকরা উত্তেজনায় হাত নাড়ছে, কিন্তু কেউ কোনও শব্দ করছে না।
হঠাৎই গনিরাম বুকের বাঁ-দিকটা খামচে ধরল। একটু যেন ঝুঁকে পড়ল সামনে।
রোশন অবাক হয়ে ওকে দেখতে লাগল। নিতু রোশনের কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিসিয়ে জিগ্যেস করল, ‘কেসটা কী হল বলো তো?’
রোশন কোনও উত্তর দিল না। ওর সমস্ত মনোযোগ তখন গনিরামের দিকে।
গায়ের রং মাজা। স্বাস্থ্য মাঝারি। কোমর ঘিরে অল্পবিস্তর চর্বি জমেছে। বুকে কাঁচাপাকা লোম। গলায় কালো সুতোর মালায় একটা চকচকে চৌকো লকেট। ডানহাতটা বুকের বাঁ-দিকে খামচে ধরে আছে। সেই হাতের দু-আঙুলে দুটো আংটি : একটা মেটালের, আর-একটা লালচে পাথর বসানো।
চোখ তুলে মুখের দিকে তাকাল।
মাথার চুল সাধারণ। তারই কিছুটা কপালে নেমে এসেছে—ঘামে ভিজে লেপটে আছে। চোখের অবস্থা কালো কাপড়ের পটির জন্য বোঝা না গেলেও নাক আর ঠোঁট কুঁচকে গেছে যন্ত্রণায়। ঠোঁটের কোণ দিয়ে লালা গড়িয়ে পড়ছে। সারা মুখে ঘামের বিন্দু। রগের পাশ দিয়ে যে-ঘামের ধারা নেমেছে সেটা কালো কাপড়টা চুষে নিচ্ছে।
‘আঃ।’ যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল গনিরাম। তারপরেই কাটা গাছের মতো মেঝেতে আছড়ে পড়ল। তখনও ও বুকের বাঁ-দিকটা খামচে ধরে আছে।
দর্শকের দল একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল—আশঙ্কার চিৎকার। গনিরামের কিছু একটা হয়েছে।
রোশন স্পষ্ট বুঝল, গনিরামের হার্ট অ্যাটাক হয়েছে।
ন’বছর আগে এক রবিবার সকাল দশটা দশে ঠিক এইরকম দৃশ্যই ও চোখের সামনে দেখেছিল। ওর বাবা একটা টুলে বসে বাঁ-হাতে একটা স্টিলের থালা নিয়ে লুচি-বেগুনভাজা খাচ্ছিলেন। একটু দূরে মেঝেতে বসে রোশন একটা গরম লুচি ছিঁড়ে তাতে বেগুনভাজার পুর দিয়ে রোল তৈরি করছিল—তাতে সাধের কামড় বসাবে বলে।
এরকম জলখাবার ওদের ঘরে কদাচিৎ হয়। নইলে রোজকার আইটেম তো সেই হাতে তৈরি আটার রুটি আর কুচো আলুর ঝোলা তরকারি!
রোশন লুচি-বেগুনভাজায় প্রথম কামড় বসানোর মুহূর্তে ঘটনাটা ঘটেছিল। দৃশ্যটা এখনও অনুপুঙ্খভাবে ওর মনে আছে।
বাবার মুখটা যন্ত্রণায় কুঁচকে গিয়েছিল। তার পরের মুহূর্তেই বাবার হাত থেকে জলখাবারের থালাটা পড়ে গিয়েছিল—অথবা বাবা ফেলে দিয়েছিলেন। কারণ, তার পরের সেকেন্ডেই বাবা দু-হাতে বুকের বাঁ-দিকটা খামচে ধরেছিলেন। যন্ত্রণার একটুকরো শব্দ ‘আঃ!’ বেরিয়ে এসেছিল বাবার মুখ থেকে। তারপরই ভারী চেহারার খাটো মানুষটা টুল থেকে ‘দড়াম’ করে পড়ে গিয়েছিল মেঝেতে।
স্টিলের থালাটা পড়ে যাওয়ার শব্দ পেয়েই মা পাশের রান্নাঘর থেকে ‘কী হল? কী হল?’ চিৎকার শুরু করে দিয়েছিল। তারপর রান্নাঘর থেকে ছুটে চলে এসেছিল এ-ঘরের দরজায়।
বাবার মেঝেতে পড়ে যাওয়ার সেই ভয়ংকর দৃশ্যটা মা দেখতে পেয়েছিল। এবং সেই মুহূর্তে মা যে-বুকফাটা চিৎকার করে উঠেছিল সেটা এখনও রোশনের কানে বাজে। আচমকা বেজে ওঠা সাইরেনের তীব্র শব্দ যেন। সর্বহারা আন্তরিক হাহাকার।
মেঝেতে পড়ে যাওয়ার আগেই রোশনের বাবা হয়তো শেষ নিশ্বাস ফেলেছিলেন। কারণ, মেঝেতে পড়ে থাকা শরীরটা ছিল নিথর। তাই মানুষটাকে আর হাসপাতালে ভরতি করা যায়নি।
রোশনের বয়স তখন আঠেরো বছর। ছোট ভাই কুশান তার দু-বছর আগেই ওদের ছেড়ে চলে গেছে।
গনিরাম বুকে হাত চেপে পড়ে যাওয়ার সময় ন’বছর আগের দৃশ্যটাই রোশনের চোখের সামনে চলে এসেছিল। তাই ও ভাবছিল, গনিরাম কি এখনও বেঁচে আছে?
পলান তখন রিং-এর ভেতরে ঢুকে পড়েছে। ডানহাতটা পতাকার মতো ওপরে তুলে চিৎকার করে বলছে, ‘আস্তে! আস্তে! সবাই চুপ করুন—একদম চুপ! ভয়ের কিচ্ছু নেই। আমরা দেখছি কী হয়েছে…।’
রোশনের ভেতরটা কেমন উতলা হয়ে উঠল। গনিরামকে যদি এক্ষুনি কোনও নার্সিংহোম বা হসপিটালে নিয়ে যাওয়া যায় তা হলে হয়তো মানুষটা বেঁচে গেলেও যেতে পারে। যদি অবশ্য গনিরাম এখনও বেঁচে থাকে।
রোশন ব্যস্ত হাতে ভিড় সরিয়ে রিং-এর পাঁচিলের কাছে পৌঁছে গেল। নিতু ওর ঠিক পিছনে।
গনিরাম নিথরভাবে পড়ে রয়েছে। ওর চোখের বাঁধন পলান খুলে দিয়েছে। উবু হয়ে বসে ওর নাকের কাছে হাত রেখে বুঝতে চেষ্টা করছে নিশ্বাস পড়ছে কি না। কবজি ধরে পালস দেখছে। বুকে কান পেতে ধুকপুকুনি আছে কি না শোনার চেষ্টা করছে।
কিছু একটা গোলমাল যে হয়েছে সেটা কামাল আঁচ করেছিল। তাই ও লড়াইয়ের ডাক থামিয়ে চোখের পটি খুলে ফেলেছে। এখন ও-ও পলানের পাশে উবু হয়ে বসে গনিরামকে ডাকছে : ‘গনিদা! অ্যাই গনিদা! কী হল তোমার? চোখ খোল। তাকাও—।’
কিন্তু গনিরাম সে-ডাকে সাড়া দিল না।
কামাল পলানের দিকে তাকিয়ে একটু থতিয়ে জিগ্যেস করল, ‘পলানদা, কেসটা…মানে, গনিদাটা…আমি তো সেভাবে ওকে হিট করিনি…।’
পলান কামালের কথার কোনও জবাব না দিয়ে রিং-এর পাঁচিল ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকা লোকজনের দিকে তাকাল। সেখানে নগেন আর কানুয়াকে দেখতে পেয়ে ইশারায় কাছে ডাকল।
ওরা দুজন নিমেষের মধ্যে রিং-এর পাঁচিল টপকে পলানের পাশটিতে হাজির হয়ে গেল।
রোশন উৎকণ্ঠা নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। গনিরামকে একবার পরীক্ষা করে দেখার জন্য ওর মন ছটফট করছিল। ও পালস দেখতে জানে। জানে যে, ঘাড়ের পাশে কিংবা রগের কাছে এমন শিরা আছে, যেগুলো মানুষ মরে গেলে আর দপদপ করে না। ও যখন ট্যাক্সি চালাত তখন ওর এক ডাক্তারি পড়া বন্ধু এগুলো ওকে শিখিয়েছিল।
চারপাশের দর্শকরা পলানের হুকুমে প্রথমটায় চুপ করে গেলেও এখন তাদের গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। তবে বেশিরভাগ দর্শক, যারা কোনওরকম বাজি ধরেনি, গোডাউন ছেড়ে চলে যেতে লাগল।
নিতু রোশনের কানে-কানে চাপা গলায় বলল, ‘চলো, চলে যাই…।’
রোশন মাথা নাড়ল, বলল, ‘না, যাব না। গনিরামের ছেলেটা ওপাশে রয়েছে না! ববিন…।’
নিতুয়া লজ্জা পেয়ে গেল। গনিরাম ওর পড়শি…কতদিনের চেনা! রোশন ওর কেউ নয়…আজই গনিকে প্রথম দেখছে। অথচ…।
পলান গনিরামের পাশ থেকে উঠে দাঁড়াল। ডানহাতটা ওপরে তুলে চেঁচিয়ে বলল, ‘আপনারা শান্ত হোন। চুপ করুন। ভয়ের কিছু হয়নি। আমাদের ফাইটার গনিরাম সেন্সলেস হয়ে গেছে। আপনারা আপনাদের বাজির টাকা বুকির কাছ থেকে রিটার্ন নিয়ে নিন।’ পলান কথাগুলো বলছিল বটে, কিন্তু সেগুলো ওর নিজের কানেই কেমন ফাঁকা আওয়াজের মতো শোনাচ্ছিল। কারণ, ও গনিরামকে নিয়ে এতক্ষণ যেসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছে তার সবক’টাতেই গনিরাম ফেল করে গেছে। পলানের গলাটা কেমন শুকিয়ে যাচ্ছিল। কী বলবে এখন?
তেমন কোনও কথা খুঁজে না পেয়ে পলান বলে উঠল, ‘আপনারা সবাই যার-যার বাড়ি চলে যান। এখন আর কোনও ফাইট হবে না। আমরা গনিরামকে নিয়ে এখন হসপিটালে যাব। আর-শনিবারে আবার ফাইটের প্রোগ্রাম হবে। এবার ভিড় পাতলা করুন…চলুন, চলুন!’
রোশনের মনটা অনেকক্ষণ ধরেই কু-ডাক ডাকছিল। এবার ও আর স্থির থাকতে পারল না। একলাফে পাঁচিল টপকে একেবারে রিং-এর ভেতরে গনিরামের পাশে। তারপর পড়ে থাকা মানুষটাকে ও নানানভাবে পরীক্ষা করতে শুরু করল।
দশসেকেন্ডের মধ্যেই রোশন বুঝতে পারল ববিন ছেলেটা অনাথ হয়ে গেছে।
রোশন উবু হয়ে বসে ছিল। চোখ তুলে তাকাতেই পলানের সঙ্গে চোখে চোখ। পলান ওর দিকে তাকিয়ে ভুরু কুঁচকে অপেক্ষা করছে।
রোশন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা নাড়ল : ‘গনিরাম মারা গেছে…হার্ট অ্যাটাক।’
‘তা হলে তো হসপিটালে নিয়ে গিয়ে কোনও লাভ নেই।’ পলান নীচু গলায় বলল, ‘হার্ট অ্যাটাক হবি তো হবি আমাদের ফাইট সেন্টারে!’
‘ওর বডিটা এখন বাড়িতে নিয়ে যেতে হবে। সেখানে নেওয়ার পর একজন ডাক্তারকে ডাকতে হবে—ডেথ সার্টিফিকেট লেখাতে হবে…।’ রোশন উঠে দাঁড়াল।
কাটা নগেন আর কানুয়া এতক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল। হয়তো বসের কোনও হুকুমের জন্য অপেক্ষা করছিল। রোশনের কথায় একটু গার্জেন টাইপের ছাপ আছে বলে কাটা নগেনের মনে হল। ও সামান্য ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, ‘সেসব রুল পলানদা জানে। আপনাকে আর নলেজ দিতে হবে না…।’ পলানের দিকে তাকাল নগেন : ‘পলানদা, তোমার রুল ফলো করে কিছুক্ষণ বিফোর একেই ছানবিন করেছি। এরিয়ায় নতুন…।’
‘সেটা একবার দেখেই বুঝেছি। নতুন ম্যাপ…।’ পলান কথাগুলো বলল রোশনের দিকে তাকিয়ে।
‘নাম রোশন। বিশ্বদার লজে উঠেছে…।’ নগেন তখনও ওর তথ্যভাণ্ডার উজাড় করছিল।
‘ওসব নিয়ে পরে কথা বলা যাবে।’ রোশন পলানকে বলল, ‘এখন একটু জলদি করুন। পুলিশ যদি একবার জানতে পারে গনিরাম এখানে ফাইট করার সময় মারা গেছে, তা হলে কিন্তু পুলিশ কেস হয়ে যাবে! আর ডেথ সার্টিফিকেট দেওয়ার সময় ডাক্তারবাবুকে দিয়ে লেখাতে হবে যে, গনিরাম বাড়িতে হার্টফেল করে মারা গেছে। এখন প্লিজ, তাড়াতাড়ি করুন—।’ রোশন প্রায় অনুনয়ের সুরে বলল।
‘গনিরাম কোথায় থাকে রে?’ পলান কানুয়াকে জিগ্যেস করল।
‘ওই তো, বারো নম্বরে…রেল লাইনের ধারে…।’
রিং-এর পাঁচিলের ওপাশে দাঁড়িয়ে থাকা নিতুর দিকে আঙুল দেখাল রোশন, ‘ওই যে, নিতুদা। উনি গনিরামের পাড়ায় থাকেন—বাড়ি চেনেন।’
কাটা নগেন আর কানুয়া ঠোঁট টিপে হাসল। বোধহয় রোশনের ‘নিতুদা’ সম্বোধনের জন্য।
পলান নিতুয়াকে ভালো করেই চেনে। কারণ, নিতু একসময় হাইরোডের বাসে পকেটমারি আর উঠাইগিরার লাইনে ছিল।
ও পকেট হাতড়ে কয়েকটা পাঁচশো আর একশো টাকার নোট বের করে কানুয়ার হাতে দিয়ে বলল, ‘যা, জলদি একটা চারশো সাত গাড়ি ধরে নিয়ে আয়। বডিটা যাবে—সঙ্গে আরও লোকজন। তুই আর নগেন মিলে কেসটা সালটে আমাদের ঠেকে চলে আয়। আর এখান থেকে বডি নিয়ে স্টার্ট দেওয়ার সময় গোডাউন ফাঁকা করে তালা মেরে দিয়ে যাবি…।’
কানুয়া ঘাড় নাড়ল।
পলান আবার বলল, ‘এখান থেকে রোশন, নিতুয়া এদের গাড়িতে তুলে নিবি…ও, হ্যাঁ—আর এই বডিটা। আমি বাইক নিয়ে বেরিয়ে গেলাম—।’
পলান রিং-এর বাইরে চলে গেল।
নগেনের সঙ্গে কীসব কথা-টথা বলে কানুয়া তাড়াহুড়ো করে রওনা হল।
রোশন ভাবছিল, নিয়তি কী অদ্ভুত!
আজ বিকেলে যখন ও বাস থেকে হাইরোডে নামল, তখন ও বুঝতেই পারেনি মাত্র কয়েক ঘণ্টা পর একটা মৃতদেহের সামনে ও দাঁড়িয়ে থাকবে। হয়তো সেই মৃতদেহের সৎকারের আয়োজনেও ওকে শামিল হতে হবে।
অথচ সেই মানুষটাকে ও চেনে না—মানে, চিনত না!
একটা দশ-বারো বছরের বাচ্চা ছেলের জন্য ওর খারাপ লাগছে।
ববিন। এইমাত্র ছেলেটা ওর বাবাকে হারিয়েছে। ছেলেটাকে রোশন দূর থেকে একঝলক দেখেছে মাত্র। ওর না হয়েছে কোনও কথা, না হয়েছে কোনও পরিচয়। অথচ ববিনের এখন কী হবে, সেটা ভেবেই ও অস্থির!
মনে-মনে এই ব্লাইন্ড ফাইটকে দোষ দিল রোশন। গোডাউনটায় প্রত্যেক শনিবার এরকম অদ্ভুত ফাইটের আয়োজন যদি না হত, তা হলে হাইরোডের চায়ের দোকানের মালিক যোগেনদা ওকে এই ফাইট দেখতে আসার জন্য বলতেন না।
এই ফাইটটার সত্যি কি কোনও দরকার আছে? কার উপকারে লাগছে এটা?
প্রথমত এটা পলানের উপকারে লাগছে, কারণ এটা ওর একটা রোরিং বিজনেস। আর পাবলিক? ফাইটের জুয়াতে আজ জিতছে, কাল হারছে। আজ হাসছে, কাল কাঁদছে। আর পলান যখন নিয়ম করে প্রত্যেক সপ্তাহে শুধু লাভই গোটাচ্ছে তা হলে বেশিরভাগ পাবলিকই কাঁদছে। এটা স্রেফ যোগ আর বিয়োগের অঙ্ক।
এবারে বাকি রইল শুধু ফাইটাররা। ওদের পক্ষে একটা লাভ : জিতলে লাভ বেশি, হারলে কম। কিন্তু ওরা তো অল্পবিস্তর চোট-আঘাতও পাচ্ছে। গনিরাম আজ এই ফাইটে নাম না লেখালে হয়তো আর ক’টা ঘণ্টা, কি ক’টা দিন, অথবা কয়েক সপ্তাহ বেশি বাঁচত। বাবাকে সে-ক’টা দিন বেশি পেত ববিন।
রোশনের ভেতরে এই বিচিত্র টানাপোড়েন চলছিল। চলতেই লাগল।
হঠাৎই কী হল, ও কাটা নগেনকে বলল, ‘আমি একমিনিট আসছি…।’
নিতুকে হাত নেড়ে বলল, ‘নিতুদা, তুমি ববিনকে তোমার কাছে নিয়ে নাও। এখনই বাচ্চাটাকে খারাপ খবরটা দিয়ো না। আমি একমিনিটের মধ্যে আসছি…।’
রোশন রিং থেকে বেরিয়ে প্রায় ছুটে গোডাউনের বাইরে চলে এল।
ওই তো, গোডাউনের বাঁ-দিকে দাঁড় করানো বাইকগুলোর মধ্যে একটা বাইকে পলান চড়ে বসেছে। বসে স্টার্ট দিচ্ছে। বাইকের হেডলাইট জ্বলছে।
বাইকটা এবার গোডাউনের দরজা পেরিয়ে খানিকটা খোলা জমি ডিঙিয়ে পিচরাস্তায় গিয়ে পড়বে।
বাইকটা এগিয়ে আসতে লাগল। এগোতে লাগল। রোশনের দিকেই আসছে। রোশনের গায়ে হ্যালোজেন হেডলাইটের আলো এসে পড়েছে।
রোশন বড়-বড় ভিজে ঘাসের ওপরে দাঁড়িয়ে ছিল। কলাবতীর দিক থেকে বাতাস আসছে। শরীরে যেন ঠান্ডা কিছু স্প্রে করছে কেউ।
রোশন হাত তুলে বাইকটাকে থামতে ইশারা করল। একটু ইতস্তত করে ডেকে উঠল, ‘পলানদা!’
বাইকটা রোশনের সামনে এসে দাঁড়াল। পলানের ডান পা মাটিতে ঠেকানো। মোটরবাইক গরগর করছে। পলান তাকিয়ে রয়েছে রোশনের দিকে। চোখে জিজ্ঞাসা।
রোশন ইতস্তত করে বলল, ‘পলানদা, একটা কথা ছিল…।’
পলান কোনও কথা বলল না—রোশনের দিকে তাকিয়েই রইল। অপেক্ষা করতে লাগল। বাইকের একটা হাতলে ঘন-ঘন মোচড় দিচ্ছিল আর বাইকটা তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে উঁচু বা নীচু পরদায় গরগর করেই যাচ্ছিল।
কথাটা বলবে, নাকি বলবে না? রোশন দোটানায় দুলছিল। মনে কিছুটা অস্বস্তি আর আশঙ্কা থাকলেও ওর মন যে ভীষণ বলতে চাইছে কথাটা!
শেষ পর্যন্ত বলেই ফেলল : ‘এই ব্লাইন্ড ফাইটটা বন্ধ করা যায় না, পলানদা?’
প্রশ্নটা শোনার পর কয়েকসেকেন্ড চুপ করে রইল পলান। তারপর একটু হেসে বাইক ছুটিয়ে চলে গেল।
রোশন বোকা-বোকা দৃষ্টিতে সেই চলে যাওয়া দেখল।
হঠাৎই ও খেয়াল করল, গোডাউনের দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে নিতু। ওকে ডাকছে।
‘রোশন, চলে এসো। ববিনটা বড্ড কাঁদছে। ওকে বলেছি, ওর বাবার অসুখ করেছে—তাই অজ্ঞান হয়ে গেছে। কিন্তু ছেলেটা মানছে না…কাঁদছে তো কাঁদছেই…।’ কথাটা বলে নিতু আবার গোডাউনের ভেতরে ঢুকে গেল।
রোশন মুখটা নীচু করে পায়ে-পায়ে গোডাউনের ভেতরে ঢুকল।
তার কিছুক্ষণ পরেই নগেনের ফোনে কানুয়ার ফোন এল। ও গাড়ি পেয়ে গেছে। আর দু-মিনিটের মধ্যেই ও চারশো সাতটা নিয়ে গোডাউনের সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে।
গোডাউন এখন মোটামুটি ফাঁকা হয়ে গেছে। গনিরামকে ঘিরে ছ’-সাতজন লোকের ভিড়। তাদের মধ্যে কেউ-কেউ গনিরামকে চিনত।
গ্রিনরুমের ভেতরে ববিনকে কোলে নিয়ে নিতুয়া একটা বেঞ্চে বসে আছে। বাচ্চাটা প্রবল কান্নাকাটি করছে। তারই মধ্যে ভাঙাচোরা স্বরে ‘বাবা! বাবা!’ করছে।
রোশন নিতুয়ার কাছে গেল। বলল, ‘নিতুদা, দাও, ববিনকে দাও। গাড়িটা না আসা পর্যন্ত আমি ওকে একটু নদীর পাড় থেকে ঘুরিয়ে নিয়ে আসি…।’
তারপর ববিনের দিকে দু-হাত বাড়িয়ে ওকে ডাকল, ‘আয়, আমার কাছে আয়…।’
ববিনকে নিয়ে গোডাউনের বাইরে বেরিয়ে এল রোশন। নদীর হাওয়া ওর চোখেমুখে এসে লাগল।
ও বুঝতে পারছিল, ওর জীবনের ভেতরে নতুন আর-একটা জীবন ধীরে-ধীরে জায়গা করে নিচ্ছে।
কিন্তু ও না শেকল ছেঁড়া পথিক! সম্পর্কহীন দায়দায়িত্বহীন মানুষ! তা হলে এসব কী হচ্ছে?
নিজের কাণ্ডকারখানা দেখে রোশন নিজেই বেশ অবাক হয়ে যাচ্ছিল।
‘আশাপুর লজ’-এর ছাদে দাঁড়িয়ে ছিল রোশন। পুবের আকাশে সূর্যের ঘুম সবে ভেঙেছে। লালচে আভা ছড়িয়ে পড়েছে সব জায়গায়। লজের ভাঙা মলিন জীর্ণ ছাদে যেমন সেই আলো লুটিয়ে পড়েছে তেমনই সেই আলোর আদরের ছোঁয়া রাঙিয়ে দিয়েছে ছাদের কয়েকটি টবে লাগানো ফুলগাছের সাদা ফুলগুলোকে।
ছাদের চওড়া পাঁচিলের ওপরে পাশাপাশি রাখা চারটি শ্যাওলা ধরা টব। টবের গাছে টগর, বেল, জুঁই আর গন্ধরাজ ফুল। এখন ফুলগুলো ভোরের আলোর আভা মেখে নিয়েছে, তার সঙ্গে বাতাসও।
রোশন সূর্যমুখী হয়ে দাঁড়িয়ে ব্যায়াম করছিল। ওর দু-হাতে দুটো আধলা ইট।
ছাদের এক কোণে জড়ো করে রাখা আট-দশটা ইট। তার কোনওটা গোটা, কোনওটা আধলা। তবে সবগুলোই ময়লা এবং শ্যাওলা মাখা। সেখান থেকে দুটো জুতসই আধলা ইট বেছে নিয়ে রোশন ব্যায়াম করছিল। রোজ সকালে আধঘণ্টা ব্যায়াম করাটা ওর অভ্যেস। ব্যায়ামের কোনও সরঞ্জাম ওর লাগে না। যেখানে যেমন জিনিস জোটে সেগুলোকেই কাজে লাগিয়ে নেয়। কখনও ইটের টুকরো, কখনও এক লিটার কি দু-লিটার জলভরা প্লাস্টিকের বোতল, কখনও বা ঢালাইয়ের রড, কিংবা স্রেফ বালি।
রোশনের গায়ে ছাই রঙের শর্টস আর সাদা স্যান্ডো গেঞ্জি। একটু দূরে ছাদের মেঝেতে রয়েছে ওর হাতঘড়ি আর ছোট ট্রানজিস্টর রেডিয়ো। রেডিয়োতে কোনও একটা এফ-এম চ্যানেলে গান বাজছে। সেটা রোশনের ব্যায়ামের রিদম-এর কাজ করছে।
‘আশাপুর লজ’ বাড়িটা বেশ পুরোনো। মাঝারি মাপের দোতলা বাড়ি—তার তিনতলায় ছাদ। বাড়িটার পাশে বড় মাপের একটা ফাঁকা জমি খাটো পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। হয়তো কোনও এককালে কেউ কিনে পাঁচিল দিয়ে ঘিরে রেখেছিল। তবে জমিটা এখন আর ঠিক ফাঁকা নেই—এলোমেলো গাছপালা আর আগাছায় ভরতি। এ ছাড়া রয়েছে একটা দরমার ঘর। ঘরটা জমির একটু ভেতরদিকে।
দরমার ঘরটা ছাড়াও জমিটার ডানদিকের কোণ ঘেঁষে একটা ছোট্ট মন্দির রয়েছে। মন্দিরটার উচ্চতা বড়জোর ফুটচারেক হবে। তার চারচালা চুড়োটা লাল রঙের, বাকি দেওয়ালগুলো সাদা। মন্দিরটা দেখে অবহেলায় পরিত্যক্ত বলে মনে হলেও সেখানে মাঝে-মাঝে ফুল-টুল পড়ে, ধূপকাঠিও জ্বলে।
মন্দিরের ভেতরে হনুমানজির একটি ছোটখাটো মূর্তি আছে। তার চারপাশে ছড়িয়ে আছে কিছু শুকনো ফুল, আর একটা মাটির থালায় রয়েছে দু-একটা বাতাসা, কয়েকটা নকুলদানা। সেখানে ঘোরাফেরা করছে ছোট-ছোট কালো পিঁপড়ে।
এই ছোট্ট নগণ্য মন্দিরটাকে সবাই বলে হনুমানজির মন্দির। আর গাছপালা, আগাছায় ভরা ফাঁকা জমিটাকে বলে ‘হনুমানজির মাঠ’। মাঠের দরমার ঘরটায় সারাদিনে কেউ আসে না। শুধু কোনও-কোনও রাতে ওই ঘরটায় আলো জ্বলতে দেখা যায়। তখন পলান আর পলানের দলবল ওই ঘরটা ব্যবহার করে।
ব্যায়াম শেষ করে আধলা ইট দুটো জায়গা মতো রেখে দিল রোশন।
তারপর প্যান্টে হাত ঘষে নিয়ে ছাদে পায়চারি করতে লাগল। ওর স্যান্ডো গেঞ্জি ঘামে ভিজে গেছে। তার ওপরে বাতাসের ছোঁয়ায় ঠান্ডা-ঠান্ডা ভাব।
এর মধ্যে আশাপুরে রোশনের চার-চারটে রাত কেটে গেছে। প্রতিদিন ভোরে ও লজের ছাদে ওঠে ব্যায়াম করার জন্য। তখন ও ঘুমিয়ে থাকা আশাপুরকে দেখতে পায়। ঠিক যেন একটা বাচ্চা ছেলে—মুখে বুড়ো আঙুল ঢুকিয়ে ঘুমিয়ে আছে। তারপর একসময় বাচ্চাটার ঘুম ভাঙে।
যত দিন গড়ায় বাচ্চাটা ততই বড় হয়ে ওঠে। তারপর সন্ধ্যা নামে। বাচ্চাটা ক্রমশ দুরন্ত হয়, দুষ্টু হয়।
ধীরে-ধীরে রাত আসে। দুষ্টু বাচ্চাটাও তার সঙ্গে-সঙ্গে বদমায়েশ হয়ে ওঠে। তারপর রাত বাড়তেই বাচ্চাটা শয়তানে বদলে যায়। এ ক’দিনে রোশন এই বদলে যাওয়ার নানান ইশারা পেয়েছে।
ছাদের পাঁচিলের কাছে এসে রোশন হনুমানজির মাঠের দিকে তাকিয়ে ছিল। গাছপালার পাতার ফাঁক দিয়ে দরমার ঘর, হনুমানজির মন্দির অল্পস্বল্প দেখা যাচ্ছিল। রোশন আনমনে এসব দেখছিল আর আশাপুর নামের বাচ্চাটার আজব রূপান্তরের কথা ভাবছিল।
কাকের ডাক কানে আসছিল অনেকক্ষণ ধরেই। কালো-কালো পাখিগুলোকে দেখাও যাচ্ছিল। এখন হনুমানজির মাঠের এই গাছপালার দিকে তাকিয়ে রোশন অন্যরকম কয়েকটা রঙিন পাখি দেখতে পাচ্ছিল। বাঁশপাতি, বসন্তবৌরি, বেনেবউ। গাছের ডালে, গাছের পাতার ফাঁকে বসে আছে। কখনও বা এদিক-ওদিক উড়ে যাচ্ছে।
দোয়েলের শিস শুনতে পাচ্ছিল রোশন। দেখতে পাচ্ছিল টুনটুনির ছটফটে লাফালাফি।
এই পাখিগুলো আশাপুরকে অনেক সুন্দর করেছে। কিন্তু দরমার ঘরটার দিকে তাকিয়ে রোশনের কপালে ভাঁজ পড়ল। এই দরমার ঘরটা সম্পর্কে এ পর্যন্ত যা শুনেছে তাতে ঘরটা কর্কশ ডাকওয়ালা কালো-কালো পাখিগুলোর চেয়ে কিছু কম খারাপ নয়।
আকাশের দিকে চোখ তুলল রোশন। এর মধ্যেই সূর্যের আলো অনেকটা বেড়ে গেছে—আর তাকিয়ে থাকা যাচ্ছে না লাল বলটার দিকে। আলোর সঙ্গে বেড়ে গেছে তেজও।
এবার নীচে নামতে হবে। স্নান-টান সেরে ব্রেকফাস্ট খাওয়ার জন্য বাইরে বেরোতে হবে। ব্রেকফাস্ট মানে লুচি-তরকারি। লজ থেকে বেরিয়ে বাঁ-দিকে এক-দু-মিনিট পা চালালেই মিষ্টির দোকান ‘মোহন সুইটস’। সেখানে মিষ্টির পাশাপাশি শিঙাড়া, নিমকি, লুচি-তরকারি এসব পাওয়া যায়। এই কয়েকটা দিন রোশন ব্রেকফাস্টের ব্যাপারটা ‘মোহন সুইটস’-এই সেরেছে। দোকানের মালিকের সঙ্গে একটু-আধটু আলাপ-টালাপও হয়েছে।
হাতঘড়ি আর রেডিয়োটা ছাদের মেঝে থেকে তুলে নিল রোশন।
রেডিয়ো অফ করে সিঁড়ি দিয়ে সাবধানে নামতে লাগল। সাবধানে, কারণ সিঁড়ির ধাপগুলো ক্ষয়াটে, ছাল ওঠা, এবং একটার সঙ্গে একটার মাপের মিল নেই।
ঠিক তখনই আওয়াজটা শুনতে পেল।
শক্ত কোনও জিনিসের সঙ্গে শক্ত আর-একটা জিনিসের সংঘর্ষের শব্দ।
কয়েকসেকেন্ড পর শব্দটা শোনা গেল আবার।
রোশন একটু তাড়াতাড়ি নামতে চেষ্টা করল। আন্দাজে বুঝতে পারল আওয়াজটা আসছে একতলা থেকে।
‘আশাপুর লজ’-এ রোশনকে নিয়ে বোর্ডার এখন মাত্র তিনজন। এবং এই তিনজনেরই থাকার ঘর দোতলায়। একতলায় শুধুমাত্র বিশ্বরূপবাবু থাকেন। এ ছাড়া কলতলা, বাথরুম, দুটো ছোট মাপের স্টোর রুম, আর রাস্তার দিকের একটা ঘর। সেটা রোশন সবসময় তালাবন্ধই দেখেছে। বিশ্বরূপবাবুকে ও জিগ্যেস করেছিল ওটাও স্টোর রুম কি না। তাতে উত্তর পেয়েছে, ‘না, ওটা স্টোর রুম নয়—তবে বলতে পারেন স্টোর রুম টাইপেরই কিছু…।’
ব্যাপারটা রোশনের কাছে স্পষ্ট হয়নি। কিন্তু তাই বলে আর কিছু জিগ্যেসও করেনি। কিন্তু পরে জেনেছে, ওই ঘরটা পলানরা ব্যবহার করে। ও-ঘরে পলানদের আর্মস থাকে। আবার কখনও-কখনও ওরা সেখানে আড্ডা দেয়, জুয়া খেলে।
দোতলায় নেমে রোশন দেখল একজন বোর্ডার একতলার আওয়াজ শুনে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এসেছে। ফরসা, বেঁটে, গোলগাল মুখ। ঠোঁটের ওপরে টুথব্রাশ গোঁফ। পরনে শুধু নীল রঙের একটা লুঙ্গি এবং কিছুটা মলিন হয়ে যাওয়া পইতে। কাঁচা ঘুম ভেঙে বুকে-পেটে হাত বোলাতে-বোলাতে বেরিয়ে এসেছে। কপালে বিরক্তির ভাঁজ। মাথার চুল এলোমেলো খোঁচা-খোঁচা।
ভদ্রলোকের সঙ্গে একদফা আলাপ হয়েছে রোশনের। কিন্তু কী যেন নামটা? এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না।
বিশ্বরূপ জোয়ারদারের লজটা বেশ পুরোনো আমলের বাড়ি। বাড়িটার সারা গা ছাল-টাল ওঠা হলেও মামুলি সাদা চুন রং করে চেহারা ফেরানোর চেষ্টা করা হয়েছে।
বাড়ির ভেতরে চৌকো উঠোন। তারই একপাশে চৌবাচ্চা, কলতলা, বাথরুম। উঠোনের মেঝেতে মাকড়সার জালের মতো ফাটল। আর কলতলার কাছটা শ্যাওলা ধরা।
দোতলায় রেলিং ঘেরা চৌকো বারান্দা—ঠিক উঠোনের মাপে। রেলিং বলতে সরু-সরু লোহার শিক। আর শিকের মাথায় রং-পালিশ চটে যাওয়া কাঠের আড়া। সেই আড়ার ওপর দিয়ে ঝুঁকে পড়ে ফরসা বোর্ডারটি একতলার শব্দের উৎস খোঁজার চেষ্টা করছে।
সিঁড়ি নামার সময় তার সঙ্গে রোশনের চোখাচোখি হয়েছে। বোর্ডার ভদ্রলোক রোশনের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে ভুরু উঁচিয়ে ইশারায় জানতে চাইল, ‘কী ব্যাপার?’
উত্তরে রোশন ঠোঁট ওলটাল শুধু।
ঠিক তখনই ও তৃতীয় শব্দটা শুনতে পেল। একটা জোরালো সংঘর্ষের শব্দ। আর তার পরেই কাচভাঙার ঝনঝন শব্দ।
রোশন তাড়াতাড়ি সিঁড়ি নামতে লাগল।
একতলায় বাইরের ঘরে এসে যে-দৃশ্যটা ও দেখল তাতে অবাক হয়ে গেল।
‘আশাপুর লজ’ আসলে বিশ্বরূপ জোয়ারদারের বাপ-ঠাকুরদার বাড়ি। সেই বাড়িটায় থাকার কেউ ছিল না—একমাত্র বিশ্বরূপ ছাড়া। তাই একসময় ওঁর মনে হয়েছে, এই বাড়িতে একা-একা থাকার চেয়ে এটাকে লজে পালটে দিলে হয়। তাতে নতুন-নতুন লোকজনের সঙ্গে পরিচয় হবে, কথাবার্তা বলে বেশ সময় কাটবে, আর তার সঙ্গে টুকটাক ব্যাবসাও করা যাবে।
আশাপুরের ‘মহামায়া কটন মিল’ বেশ চালু মিল। সেই মিলটাকে ঘিরে নানারকমের কাজকারবারের পত্তন হয়েছে আশাপুরে। সেই সূত্রে বাইরে থেকে বেশ কিছু ছোট-বড় ব্যবসায়ী আশাপুরে আসে। দু-এক দিনের জন্য মাথা গোঁজার জায়গা খোঁজে।
এ ছাড়া আশাপুরের গান্ধীমাঠের কাছে প্রায় বিশ-পঁচিশটা লেদ কারখানা আছে। তাদের লেদ মেশিন, শেপার মেশিন, মিলিং মেশিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত চলে। সবসময় ইস্পাতের নানান ছাঁদের কাটাকুটি নিয়ে তারা ব্যস্ত। তাকে ঘিরে গজিয়ে উঠেছে লোহার বাবরি বা ছাঁটের ব্যাবসা। ছোট কিংবা বড় লরিতে লোড হয়ে টন-টন বাবরি চালান যায় দূরে-দূরে।
এই সব ব্যবসা ঘিরেও বাইরের লোকের আসা-যাওয়া আছে আশাপুরে। তাদের কেউ-কেউ এসে ওঠে বিশ্বরূপ জোয়ারদারের লজে। দু-চারটে দিন কাটিয়ে যায়। লজে খাওয়াদাওয়ার কোনও ব্যবস্থা নেই। তবে কাছাকাছি অনেক খাওয়ার দোকান আছে। ভাতের হোটেলও।
‘আশাপুর লজ’-এর একটা বড় গুণ আছে : খুব সহজেই বোর্ডারদের আপন করে নিতে পারে। এর কারণ, বিশ্বরূপ জোয়ারদারের ব্যবহার। সদালাপী মানুষটির মুখে সবসময় চওড়া হাসি। তার ওপর রয়েছে লজের সুবিধেজনক পকেটসই রেট। ফলে, বিশ্বরূপ জোয়ারদারের লজ কখনও একেবারে খালি যায় না। সারা বছর ধরে টুকটাক ব্যাবসা চলতেই থাকে।
লজের বাইরে একটা মাঝারি মাপের সাইনবোর্ড আছে। সেটার রং-টং চটে গেলেও ‘আশাপুর লজ’ শব্দ দুটো পড়া যায়। তার নীচে একটা ছোট বোর্ড লাগানো আছে। তাতে লেখা ‘প্রোঃ বিশ্বরূপ জোয়ারদার, বি. এ.’। বিশ্বরূপবাবুদের বংশে তিনি ছাড়া কেউ গ্র্যাজুয়েট হতে পারেনি। তাই সাইনবোর্ডে তাঁর লেখাপড়ার সাফল্যের ওরকম বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে।
সদর দরজা ডিঙিয়ে লজে ঢুকলেই একটা বড়সড় লম্বাটে ঘর। তার বাঁ-দিকে একটা বড় কাঠের টেবিল। টেবিলের ওপারে যে-হাতলওয়ালা কাঠের চেয়ারটা রাখা আছে সেটাতে বিশ্বরূপবাবু বসেন। ওঁর মাথার পিছনে দেওয়াল জুড়ে একটা বড় ইংরেজি ক্যালেন্ডার। একপৃষ্ঠা জুড়ে বারো মাসের তারিখ ছাপা। ক্যালেন্ডারটার পাশে ফ্রেমে বাঁধানো তিনটে সাদা-কালো ফটোগ্রাফ। ফটোগুলো এতই পুরোনো যে, ফটোর মানুষগুলোর চেহারা ভালো করে বোঝা যাচ্ছে না। এ ছাড়া বিশ্বরূপের টেবিল-চেয়ার দুটোর অবস্থাও তাই। হদ্দ পুরোনো হওয়ায় কাঠের রং মোটামুটিভাবে গাঢ় খয়েরি হয়ে গেছে। তার ওপর এখানে-ওখানে হাফডজন ফাটল তো আছেই।
তিনটে ফটোর নীচে পাশাপাশি দাঁড় করানো রয়েছে দুটো শো-কেস। সে-দুটোর বয়েস এত বেশি যে, স্লাইডিং পাল্লার কাচগুলো ময়লার দাপটে ঘষা কাচের চেহারা নিয়েছে। ফলে ভেতরে ঠিক যে কী-কী জিনিস রাখা আছে সেটা বোঝা বেশ শক্ত।
টেবিলে পড়ে আছে একটা জাবদা খাতা আর একটা বাংলা খবরের কাগজ। খবরের কাগজটার অবস্থা দেখে বোঝা যায় ওটা অনেকে অনেকবার পড়েছে। কারণ, ওটা গতকালের কাগজ। আজকের কাগজ এখনও আসেনি—আসার সময় হয়নি।
বিশ্বরূপ জোয়ারদারের চেয়ারের উলটোদিকে দুটো হাতল ছাড়া ছাই রঙের প্লাস্টিকের চেয়ার। বোর্ডারদের বসার জন্য। আর মালিক এবং অতিথিদের হাওয়া সাপ্লাই করার দায়িত্ব নিয়েছে একটা জোব চার্নকী সিলিংফ্যান। মাথার ওপরে হাঁপাতে-হাঁপাতে ঘুরছে এবং তার কাতরানির শব্দও শোনা যাচ্ছে।
ঘরের ডানদিকে দুটো বেঞ্চি পাতা। সেগুলোর এমনই দশা যে, অনায়াসে তাদের হেরিটেজ আইটেম বলা যায়। তারই একটার ওপরে বেশ কয়েকটা বিছানার চাদর আর তিনটে বালিশ থাকে-থাকে সাজানো রয়েছে।
এই ঘরটাকে এককালে জোয়ারদার পরিবারের লোকরা ‘বাইরের ঘর’ বলে ডাকত। আজ ঘরটার পরিচয় ‘আশাপুর লজ’-এর ‘রিসেপশন রুম’।
সিঁড়ি দিয়ে হুড়মুড় করে একতলায় নেমে এসেছে রোশন। তারপর ঢুকে পড়েছে ‘বাইরের ঘর’ অথবা রিসেপশন রুমে। এবং অবাক হয়ে গেছে। কারণ, ঘরের দৃশ্যটা সাধারণত যেরকম দেখতে ও অভ্যস্ত এখন সেরকম ছিল না।
দুটো ছেলে বিশ্বরূপবাবুর টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাদের একজনের হাতে একটা হকি স্টিক। আর-একজন বিশ্বরূপ জোয়ারদারের কলার চেপে ধরে ভীষণভাবে ঝাঁকাচ্ছে। একটা শো-কেসের দুটো পাল্লাই আর নেই—তার বদলে মেঝেতে ভাঙা কাচ ছড়িয়ে আছে।
হকি স্টিক হাতে ছেলেটা স্টিকটা মাথার ওপরে তুলল। দেওয়ালের ফটোগুলো তাক করে অস্ত্রটা চালাল।
রোশন একলাফে পৌঁছে গেল ছেলেটার পিছনে। অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় গতিশীল স্টিকটাকে শক্ত হাতে আঁকড়ে ধরল।
সিঁড়ি নামতে-নামতে রোশন হাতঘড়িটাকে শর্টস-এর পকেটে ঢুকিয়ে ফেলেছিল। কিন্তু ট্রানজিস্টর রেডিয়োটা বাঁ-হাতের মুঠোয় ধরে রেখেছিল। তাই হকি স্টিকের আঘাত থেকে বিশ্বরূপদাকে বাঁচানোর সময় শুধুমাত্র ডানহাতটাই ও ব্যবহার করতে পেরেছিল।
হকি স্টিকটা রোশন পিছন থেকে আচমকা চেপে ধরায় আক্রমণকারী ছেলেটি পিছনে টাল খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল। কিন্তু কোনওরকমে নিজেকে সামলে নিল। ওর শরীরটা আধপাক ঘুরে পেন্ডুলামের মতো এপাশ-ওপাশ দুলে উঠল দুবার। তারপর স্থির হল। কিন্তু ওর শরীরের ধাক্কায় একটা প্লাস্টিকের চেয়ার উলটে পড়ে গেল।
হকি স্টিকটা রোশনের হাতে চলে এসেছিল। একইসঙ্গে ও চেঁচিয়ে উঠেছিল, ‘থামো! থামো! কী হচ্ছে এসব! থামো বলছি!’
ছেলেটা থমকে গেল। রোশনের দিকে রক্ত-চোখে তাকিয়ে রইল। যেন এখুনি ওর ওপরে হিংস্রভাবে ঝাঁপিয়ে পড়বে।
দ্বিতীয় ছেলেটা ঝাঁকুনির কাজটা থামালেও বিশ্বরূপ জোয়ারদারের কলারটা এখনও খামচে ধরে আছে।
এই দুটো ছেলেই রোশনের অচেনা। শনিবার রাতে ব্লাইন্ড ফাইটের সময় দুটোর একটাকেও ও দেখেনি।
প্রথম ছেলেটার গায়ের রং কালো। মাথায় ছোট-ছোট চুল। গাল দুটো ডুমো-ডুমো। নাকটা বেশ লম্বা। সামনের দাঁতগুলো এত উঁচু যে, দাঁতের মাজনের জোরালো বিজ্ঞাপনের মডেল হতে পারে। পোশাক বলতে একটা কালো হাফশার্ট, আর ময়লা জিনসের প্যান্ট। পায়ে সস্তা চটি।
দ্বিতীয় ছেলেটা এখন বিশ্বরূপদার কলার ছেড়ে দিয়েছে। রোশনের দিকে ভুরু কুঁচকে কুতকুতে চোখে তাকিয়ে আছে।
ছেলেটার গায়ের রং মাঝারি। কাঁধ চওড়া। গাল ভাঙা। শৌখিন গোঁফ। দু-কানে স্টিলের মাকড়ি। গাঢ় নীল রঙের একটা রাউন্ড নেক টি-শার্ট পরে আছে। পায়ে বাদামি রঙের কর্ডের প্যান্ট। পায়ে কালো রঙের চপ্পল।
রোশন ধীরে-ধীরে বলল, ‘বিশ্বরূপদার গায়ে হাত দেবে না। ওঁর কাছ থেকে সরে যাও।’ মাথা ঝাঁকিয়ে সরে যাওয়ার ইশারা করল।
রোশনের গলার স্বর ঠান্ডা, কিন্তু তার মধ্যে একটা আদেশের ছোঁয়া ছিল।
দ্বিতীয় ছেলেটা রোশনের হাতের হকি স্টিকটার দিকে একপলক তাকাল। তারপর খানিকটা অনিচ্ছার ভাব নিয়ে বিশ্বরূপ জোয়ারদারের কাছ থেকে একটু পিছিয়ে দাঁড়াল।
প্রথম ছেলেটা রোশনকে সশস্ত্র দেখেও ঘাবড়াল না, পাত্তাও দিল না। দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বলে উঠল, ‘তুই কে রে? কোন হরিদাস? ফোট এখান থেকে! এটা আমাদের পার্সোনাল কেস—আমরা নিজেরা মিটিয়ে নেব। চ্যাল-চ্যাল, ফোট!’
দ্বিতীয় ছেলেটা বলল, ‘তুই বাইরের পাবলিক—আমাদের কেসে নাক গলালে নাক কেটে দেব—।’ হাতের পাঞ্জা দিয়ে কেটে দেওয়ার ইশারা করল দ্বিতীয়।
প্রথম ছেলেটা হঠাৎ কী ভাবল কে জানে! রোশনের মুখ লক্ষ্য করে আচমকা ঘুসি চালাল। ও ভেবেছিল হকি স্টিক দিয়ে পালটা আঘাত করে ওঠার আগেই ঘুসিটা রোশনের মুখে গিয়ে পড়বে।
দ্বিতীয় ছেলেটাও মোটামুটিভাবে একইরকম ভেবেছিল। হয়তো বিশ্বরূপ জোয়ারদারও তাই।
কিন্তু বাস্তবে ব্যাপারটা ঘটল অন্যরকম। বাঁ-হাতে ধরা রেডিয়োটা এক নিমেষে চলে এল প্রথমের ঘুসির গতিপথে। যথারীতি সংঘর্ষ হল। কিন্তু তার শব্দ তেমন জোরালো হল না। তবে রেডিয়োটা হঠাৎই বাজতে শুরু করল। মাতাল করা এক মিউজিক ভেসে বেড়াতে লাগল রিসেপশনে।
আক্রমণকারী ছেলেটা শক খাওয়ার ভঙ্গিতে ডানহাতটা ঝট করে পিছিয়ে নিল। ওর মুখ কুঁচকে গেল যন্ত্রণায়।
রোশন বলল, ‘বাইরের পাবলিক হলে কি অন্যায় দেখলে বাধা দেওয়া বারণ? বিশ্বরূপদার সঙ্গে যা কিছু গোলমাল সব আলোচনা করে মিটিয়ে নাও—গায়ে হাত-টাত তুলে নয়।’ কথা বলতে-বলতে রোশন হকি স্টিকটা বেঞ্চিগুলোর দিকে ছুড়ে ফেলে দিল : ‘তোমরা চেয়ারে বোসো। বসে কথা বলো—।’
রোশনের কথার উত্তরে ছেলে দুটো কোনও কথা বলল না। চেয়ারে বসলও না। ওদের মুখ-চোখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল, ওরা ভেতরে-ভেতরে ফুঁসছে। রোশনের হাতে এখন হকি স্টিক নেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও ওরা ঠিক করে উঠতে পারছে না রোশনকে এখন অ্যাটাক করা যায় কি না। বোধহয় রোশনের স্যান্ডো গেঞ্জির আশপাশ দিয়ে বেরিয়ে থাকা পেশির দল ওদের ধন্দে ফেলে দিয়েছিল।
রোশন রেডিয়োটা একবার দেখল। ওপরের রুপোলি রঙের প্লাস্টিক কভারটা আড়াআড়ি ফেটে গেছে। তা ছাড়া একটা ছোট তেকোণা টুকরো খসেও পড়েছে মেঝেতে।
রেডিয়োর পিছনদিকের অন-অফ সুইচটাকে খুটখাট শব্দ করে বারকয়েক নাড়াচাড়া করল, যদি ওটাকে অফ করা যায়। কিন্তু না, তাতে কোনও কাজ হল না। তখন ভলিয়ুমের রোলার সুইচটাকে নিয়ে পড়ল। আবারও রেজাল্ট জিরো।
এই কাজগুলো করতে-করতেই ও বিশ্বরূপদাকে বলল, ‘কী, বিশ্বরূপদা, ঠিক বলেছি না?’
বিশ্বরূপ জোয়ারদার বড়-বড় শ্বাস ফেলছিলেন। গলায় হাত বোলাচ্ছিলেন। রোশন ঠিক সময়ে না এসে পড়লে আরও কত হেনস্থা সহ্য করতে হত কে জানে!
এখন তিনি অবাক-বিহ্বলভাবে রোশনকে দেখছিলেন। ওর প্রশ্নের অর্থ প্রথমটায় ধরতে পারলেন না। তাই পালটা জিগ্যেস করলেন, ‘কী বলো তো?’
‘না, বলছিলাম যে, কোনও আলোচনা থাকলে সেটা বসে ঠান্ডা মাথায় সেরে ফ্যালো।’ ছেলে দুটোর দিকে তাকাল এবার : ‘জামার কলার খামচে ধরে, হকি স্টিক হাতে নিয়ে ভদ্রলোকরা কখনও আলোচনা করে না— ছোটলোকরা করে। তোমরা কি ছোটলোক?’
ছেলে দুটোকে একটু বিভ্রান্ত বলে মনে হল। ওরা ঠিক ধরতে পারছিল না রোশনের কথাবার্তা কোনদিকে এগোচ্ছে।
রেডিয়োটা ডানহাতে নিল রোশন। ওদের কাছে এগিয়ে এল। নীচু গলায় বলল, ‘নাও, এবার চট করে বসে পড়ো—।’
ছেলে দুটো দাঁড়িয়েই রইল। অপছন্দের চোখে রোশনকে দেখতে লাগল।
রোশন বিশ্বরূপ জোয়ারদারের দিকে তাকাল : ‘দাদা, আপনি অ্যাট লিস্ট বসুন। তারপর বলুন, কী ব্যাপার। এরা সাতসকালে আপনার গেস্টহাউসে এসে এরকম জানোয়ারের মতো উৎপাত করছে কেন?’
প্রথম ছেলেটা বিশ্বরূপদার দিকে কড়া চোখে তাকিয়ে বলে উঠল : ‘বিশ্বদা, আমরা এখন যাচ্ছি। কেসটা রিপোর্ট করে দিচ্ছি। বাইরের পাবলিকের চাটাচাটি আমরা টলারেট করব না। আপনি শালা ফিকিরবাজি করে আমাদের বারবার ঘোরাচ্ছেন—কিন্তু ওসব করে কোনও লাভ নেই। আমরা আবার আসব…।’
এ-কথা বলে ছেলে দুটো চলে গেল। যাওয়ার আগে রোশনকে চোখ দিয়ে মেপে গেল। সদর দরজাটা বিকট আওয়াজে ‘দড়াম’ করে খুলে এবং বন্ধ করে ওদের রাগের রিখটার স্কেলের ম্যাগনিটিউডের আইডিয়া দিয়ে গেল।
হকি স্টিকটা বেঞ্চির কাছে মেঝেতে চুপচাপ শুয়েই রইল।
‘আশাপুর লজ’-এর রিসেপশনে এখন শব্দ বলতে শুধু মাথার ওপরে ঘুরতে থাকা পুরোনো সিলিংফ্যানটার কাতরানির শব্দ, আর রোশনের বিকল রেডিয়োর মিউজিক। মিউজিকটা তখন থেকে এমন একঘেয়েভাবে বেজে চলেছে যে, এখন রীতিমতো বিরক্তিকর লাগছে।
আওয়াজটা বন্ধ করার জন্য রোশন রেডিয়োটাকে শূন্যে কয়েকবার জোরালো ঝাঁকুনি দিল। কিন্তু কোনও লাভ হল না। তখন বিরক্তির একটা শব্দ করে ও বেঞ্চির কাছে চলে গেল। থাকে-থাকে রাখা দুটো বালিশের মাঝে রেডিয়োটা গুঁজে দিল। সঙ্গে-সঙ্গে কেউ যেন আওয়াজটার গলা টিপে ধরল।
আবার বিশ্বরূপদার সামনে এসে দাঁড়াল রোশন। নরম গলায় বলল, ‘দাদা, বসুন। একটু খুলে বলুন তো, ব্যাপারটা কী…।’
বিশ্বরূপ জোয়ারদার ধীরে-ধীরে নিজের চেয়ারে বসলেন। রোশন লক্ষ করল, ওঁর রোগা হাত দুটো থরথর করে কাঁপছে।
মেঝেতে ছড়িয়ে আছে ভাঙা কাচের টুকরো। সাবধানে পা ফেলে রোশন উলটে পড়া প্লাস্টিকের চেয়ারটার কাছে গেল। সেটাকে সোজা করে তারপর টেনে নিয়ে বিশ্বরূপদার মুখোমুখি বসল। ওঁর কথা শোনার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।
‘শোনো, রোশন—আসল ব্যাপারটা হল টাকা। প্রতি সপ্তাহে ওদের হাজার টাকা করে দিতে হবে। এই হল ওদের ডিমান্ড। আগে পাঁচশো টাকা করে দিতাম—দু-সপ্তাহ হল টাকাটা ওরা বাড়িয়েছে। বাড়িয়ে হাজার টাকা করেছে। সেটা প্রতি সপ্তাহে কোত্থেকে জোগাড় করব? আমার লজ কি সেরকম চলে?’
‘ ”ওরা” মানে কারা?’
‘কারা আবার? ওই পলান নামে শয়তানটার চ্যালা-চামুণ্ডা গুন্ডা…।’
আবার সেই পলান! গোডাউনের ব্লাইন্ড ফাইট গেম শো-র ‘চেয়ারম্যান’!
‘আপনি টাকা দেন কেন?’
‘ভয়ে।’
‘ওদের ভয় পাওয়ার কী আছে?’ রোশন অবাক হয়ে জানতে চায়।
‘ভয় পাওয়ার কী আছে মানে?’ বিশ্বরূপ পালটা অবাক চোখে তাকিয়ে থাকেন অবাক হয়ে যাওয়া বছর সাতাশ-আটাশের ছেলেটার দিকে। এ-ছেলেটা কি ‘তোলা’ ব্যাপারটার কথা লাইফে শোনেনি?
বিশ্বরূপ শার্টের খুঁট দিয়ে মুখ মুছলেন। টেবিলে রাখা জাবদা খাতাটাকে অকারণেই একপাশ থেকে আর-একপাশে সরালেন। মুখ দেখে মনে হল, কী বলবেন সেটা ভাবছেন। হয়তো আরও ভাবছেন, কতটুকু বলবেন।
রোশন ‘আশাপুর লজ’-এর মালিককে দেখছিল।
মানুষটার চেহারা একেবারেই নিরীহ। দেখে বোঝা যায়, গায়ের রং এককালে ফরসা ছিল, সময়ের চাপে তামাটে হয়ে গেছে। বয়েস খুব বেশি হলে পঞ্চাশ-বাহান্ন। লম্বায়-চওড়ায় বেশ খাটোই বলতে হবে। মাথার চুল পাতলা হয়ে জমি দেখা যাচ্ছে। চুলে অল্পবিস্তর পাক ধরেছে। ছোট কপাল। কপালের বাঁ-দিক ঘেঁষে কালির ছিটের মতো তিন-চারটে তিল। চোখে প্লাস্টিক ফ্রেমের চশমা। চশমার নীচে ছোট নাক। নাকের নীচে সরু গোঁফ। এ ছাড়া পাতলা ঠোঁটের প্রান্ত দুটো ওপরদিকে সামান্য বাঁক নিয়ে শেষ হওয়ায় মনে হয় যেন বিশ্বরূপদা সবসময় হাসছেন।
গত তিনদিনে ওঁর সঙ্গে রোশনের ভালোমতোই আলাপ-পরিচয় হয়েছে। একসময় ‘আশাপুর লজ’-এর এই বাড়িটায় বিশ্বরূপ জোয়ারদারদের একান্নবর্তী পরিবার বাস করত। লোকজনের কথার্বাতা চলাফেরায় বাড়িটা সরগরম থাকত। তারপর সময়ের স্রোতে সবাই একে-একে নানানদিকে ছিটকে গেছে। কেউ চাকরি নিয়ে দেশান্তরী হয়েছে, কেউ ভাগ্য ফেরাতে শহরে পাড়ি দিয়েছে। আবার কেউ বা অকালেই ঈশ্বরের প্রিয় হয়ে গেছে। এইভাবে ভাগচক্রে ভাগ-ভাগ হয়ে শেষ পর্যন্ত বিশ্বরূপ জোয়ারদার ভাগশেষ হয়ে পড়ে আছেন। একেবারে একা। ওঁর আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব বলতে শুধুই লজের বোর্ডাররা।
লজের মালিককে খুঁটিয়ে দেখছিল রোশন। অপমানের ঝাপটায় কানদুটো এখনও লাল হয়ে আছে। রোশনের চোখে চোখ পড়লেই চোখ সরিয়ে নিচ্ছেন। এমন একটা ভাব যেন পারলে নিজের শরীরের ভেতরেই লুকিয়ে পড়তে চান।
রোশনের খুব খারাপ লাগছিল। বিশ্বরূপদার হেনস্থা, অপমান, লজ্জা—এসব ও দেখতে চায়নি। হয়তো অনেকদিন ধরেই এ ধরনের ব্যাপার চলছে। এবং ‘চলছে, চলবে’—এটাই যেন একমাত্র স্লোগান।
‘কী হল, বলুন—ভয় পাওয়ার কী আছে?’ রোশনের প্রশ্নের ঢংটা এমন যেন লাস্ট বেঞ্চের দুর্বল ছাত্রকে শাসাচ্ছে।
বিশ্বরূপ জোয়ারদার অতি কষ্টে রোশনের চোখে চোখ মেলালেন।
কোনওরকমে মিনমিন করে জবাব দিলেন, ‘ওরা সবসময় মারধোরের ভয় দেখায়। ওদের কাছে ছোরা, রিভলভার, বোমা—সব আছে…।’
‘আছে। কিন্তু ওরা তো মাত্র দশ-বারো-চোদ্দোজন। আর আপনারা তো সংখ্যায় অনেক।’
‘আপনারা মানে?’ অবাক হয়ে জানতে চাইলেন বিশ্বরূপ।
‘আপনারা মানে আপনারা—আশাপুরের লোকজন, আশাপুরের মানুষ…।’
‘মানুষ!’ হতাশায় বিষণ্ণ হাসলেন বিশ্বরূপ : ‘আমরা মানুষ হলে তো হয়েই যেত!’
‘আপনার থেকে যে উইকে হাজার টাকা করে চাইছে এ-কথা আর কেউ জানে না?’
‘জানে—সবাই জানে। কিন্তু জানলে কী হবে? সবাই তো টাকা দেয়!’
‘ব্যাপারটা তো তোলাবাজি ছাড়া আর কিছু না!’
মাথা নীচু করলেন বিশ্বরূপ জোয়ারদার। আক্ষেপের শব্দ করে হাসলেন : ‘না রোশন—তোলাবাজি বোলো না। বলো, প্রোটেকশন মানি। রেগুলার এই টাকাটা দিলে আমার লজের কোনও ক্ষতি হবে না—কেউ এটার কোনও ক্ষতি করতে পারবে না। বোঝো অবস্থা!’
‘আর কারা-কারা এরকম টাকা দেয়?’
‘বললাম যে—সবাই। প্রত্যেকটা দোকানদার—এমনকী চায়ের দোকান, পানের দোকান, রোল-চাউমিনের দোকান—কেউ বাদ নেই। এক-একজনের রেট এক-একরকম। কী বলব তোমাকে…ফুটপাথে বসে যে দোক্তাপাতা বেচে তাকেও পলানের প্রোটেকশন মানি দিতে হয়।’
‘চমৎকার!’ রোশন মুখের ভেতরে একটা তেতো স্বাদ টের পেল।
‘তুমি ওদের আটকাতে চেষ্টা করে ভালো করোনি। ওরা ফিরে আসবে—একটু পরে, কি আরও অনেক পরে…।’
‘কিন্তু বিশ্বরূপদা, আমি তো ওদের কাউকে মারিনি! শুধু থামাতে চেষ্টা করেছি। তা ছাড়া একটা ছেলে তো আপনার গায়ে হাত তুলেছিল! আপনাকে মারধোর করছিল…।’
বিশ্বরূপ জোয়ারদার রোশনকে বাধা দিয়ে বললেন, ‘মারধোর আর কোথায়! জামার কলারটা ধরে একটু ঝাঁকাচ্ছিল শুধু—।’ কথাটা বলার সময় রোশনের চোখে চোখ মেলাতে পারলেন না—চোখ সরিয়ে নিলেন।
রোশন অবাক হয়ে ওঁর দিকে তাকিয়ে রইল। মানুষটা বলছে কী! ‘কলারটা ধরে একটু ঝাঁকাচ্ছিল শুধু’!
রোশনের মনে তর্ক করার জেদ তৈরি হল। ও বলল, ‘আর হকি স্টিক দিয়ে যে ভাঙচুর চালাচ্ছিল? সেটা কী ব্যাপার?’ ইশারায় ভাঙা শো-কেস আর মেঝেতে ছড়িয়ে থাকা কাচের টুকরোগুলো দেখাল।
‘দ্যাখো, ওরা ছোট ছেলে। বয়েস কম। তো একটু দুরন্ত তো হবেই। তাই রাগের মাথায় হুড়োহুড়ি করতে-করতে…।’
‘বিশ্বরূপদা, আপনার লজ্জা করছে না?’ ভর্ৎসনা ছিটিয়ে জানতে চাইল রোশন। আচ্ছা, কোন আক্কেলে মানুষটা এইরকম কথা বলছে? ছোট ছেলে! বয়েস কম! দুরন্ত!
রোশন বুঝল এ নিয়ে কথা বাড়িয়ে আর লাভ নেই। যা হওয়ার তা হয়ে গেছে। ওর হাত থেকে তির ছুটে গেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ওর মনে হচ্ছিল, ও যা করেছে ঠিক করেছে। পলানের শাগরেদরা দুরন্ত হতে পারে, আর ও দুরন্ত হলেই দোষ!
বিশ্বরূপ জোয়ারদার রোশনের প্রশ্ন অথবা মন্তব্যের উত্তরে কোনও কথা বললেন না। টেবিলের জাবদা খাতা আর খবরের কাগজটা একবার এপাশে আর-একবার ওপাশে সরিয়ে গোছগাছের ভান করতে লাগলেন। তারই ফাঁকে সদর দরজার দিকে দুবার তাকালেন। বোধহয় ভাবছিলেন, এই বুঝি পলানের চ্যালারা ফিরে এল।
রোশন বিশ্বরূপদার দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে রইল। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, ‘আপনি ফোন করে ছোটকুকে ডেকে নিন। এখানে এই ছড়ানো কাচের ওপরে বেশি হাঁটা-চলা করবেন না। পা কেটে যেতে পারে…।’
ছোটকু বিশ্বরূপের লজে ফাইফরমাশ আর ঝাড়পোঁছের ঠিকে কাজ করে। সকালে ন’টা-সাড়ে ন’টায় একবার আসে, তারপর সন্ধে সাতটা-সাড়ে সাতটা নাগাদ আর-একবার। বছর আঠেরো-উনিশ বয়েস। এ-পাড়ার আরও কয়েকটা দোকানে ও কাজ করে। থাকে রেল লাইনের ধারের বস্তিতে। রাতে ছেলেটা একজন কেবল অপারেটরের অফিসে নাইট ডিউটি করে। সেখানে রাত জেগে ফ্রি-তে সিনেমা দ্যাখে। ওর ভীষণ সিনেমা দেখার নেশা। ছোটকুর কাছেই এসব শুনেছে রোশন।
রোশনের কথায় বিশ্বরূপ প্যান্টের পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করলেন।
‘আমি আসছি—’ বলে রোশন বেঞ্চির কাছে গেল। বালিশের ফাঁক থেকে রেডিয়োটা বের করল। তখনও যন্ত্রটা বাজছে।
রোশন রেডিয়োটা ছুড়ে ফেলে দিল। ওটা মেঝেতে পড়ে থাকা ভাঙা কাচের টুকরোগুলোর ওপরে গিয়ে পড়ল।
‘ছোটকুকে ওটা ফেলে দিতে বলবেন—।’ বলে রোশন পকেটে হাত ঢোকাল। হাতঘড়িটা বের করে সময় দেখল। আটটা কুড়ি।
অনেক দেরি হয়ে গেছে। ওর পুজোর সময় অনেকক্ষণ পেরিয়ে গেছে। ওর ব্যাগে মা, বাবা আর ছোট ভাইয়ের একটা গ্রুপ ফটো আছে। ছোটবেলা একটা সস্তার ক্যামেরা দিয়ে রোশনই ফটোটা তুলেছিল। রোজ সকালে সাড়ে সাতটা নাগাদ মেঝেতে বাবু হয়ে বসে ওই ফটোটা সামনে রেখে ধূপ কাঠি জ্বেলে রোশন পুজোয় বসে। মানে, ওদের তিনজনের কথা ভাবে। সেটাই রোশনের পুজো।
ও তাড়াতাড়ি ওপরে গিয়ে পুজোয় বসল।
আর পলান ওর দলবল নিয়ে ‘আশাপুর লজ’-এ হানা দিল ঠিক সাড়ে দশটায়। ওদের সবার হাতেই ছিল গুন্ডাগর্দির স্ট্যান্ডার্ড অস্ত্রশস্ত্র।