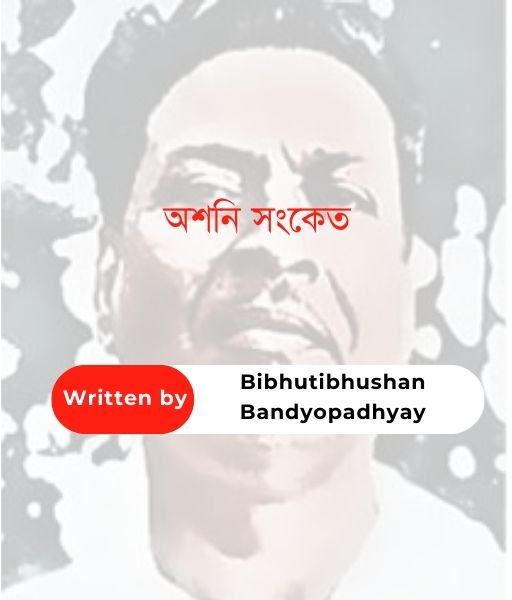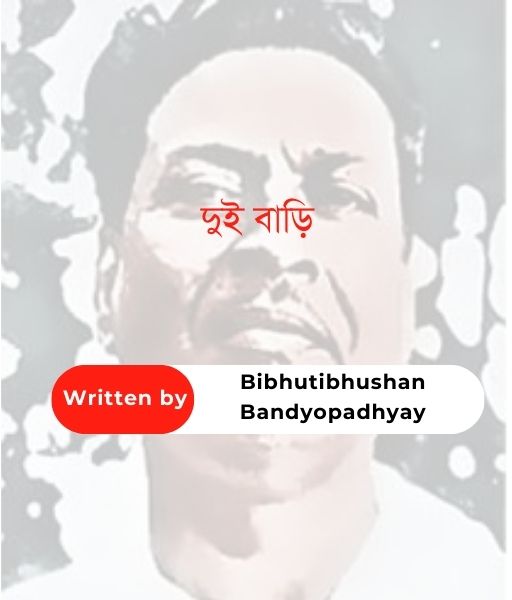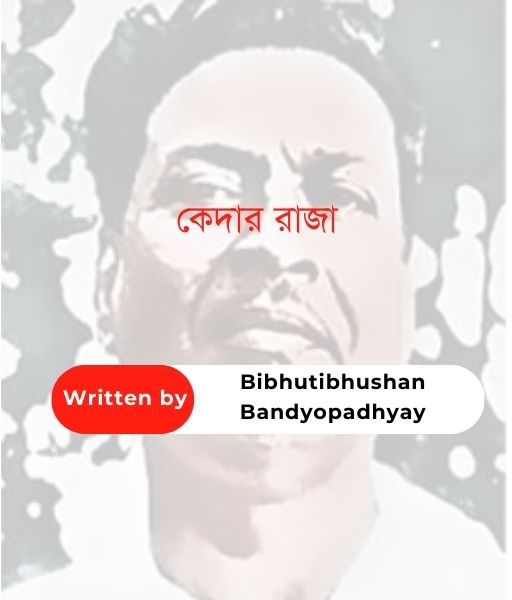জ্যাঠামশায়দের রান্নাঘরে – Drishti Pradip
০১.
জ্যাঠামশায়দের রান্নাঘরে খেতে বসেছিলাম আমি আর দাদা। ছোট কাকীমা ডাল দিয়ে গেলেন, একটু পরে কি একটা চচ্চড়িও নিয়ে এলেন। শুধু তাই দিয়ে খেয়ে আমরা দু’জনে ভাত প্রায় শেষ করে এনেছি এমন সময় ছোট কাকীমা আবার এলেন। দাদা হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে–কাকীমা, আজ মাছ ছিল যে, মাছ কই?
আমি অবাক হয়ে দাদার মুখের দিকে চাইলাম, লজ্জা ও অস্বস্তিতে আমার মুখ রাঙা হয়ে উঠল। দাদা যেন কি! এমন বোকা ছেলে যদি কখনো দেখে থাকি! আমার অনুমানই ঠিক হ’ল, কাকীমা একটু অপ্রতিভের সুরে বললেন–মাছ যা ছিল, আগেই উঠে গেছে বাবা, ওই দিয়ে খেয়ে নাও। আর একটু ডাল নিয়ে আসবো?
দাদার মুখ দেখে বুঝলাম, দাদা যেন হতাশ হয়েছে। মাছ খাবার আশা করেছিল, তাই না পেয়ে। মনটায় আমার কষ্ট হ’ল। দাদা দেখেও দেখে না, বুঝেও বোঝে না–দেখছে এখানে আমরা কি অবস্থায় চোরের মত আছি, পরের বাড়ি, তাদের হাত-তোলা দু-মুঠো ভাতে কটি ভাইবোন কোনরকমে দিন কাটিয়ে যাচ্চি, এখানে আমাদের না আছে জোর, না আছে কোনো দাবি–তবুও দাদার চৈতন্য হয় না, সে আশা করে বসে থাকে যে এই বাড়ির অন্যান্য ছেলেদের মত সেও যত্ন পাবে, খাবার সময় ভাগের মাছ পাবে, বাটি-ভরা দুধ পাবে, মিষ্টি পাবে। তা পায়ও না, না পেয়ে আবার হতাশ হয়ে পড়ে, আশাভঙ্গের দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক চায়–এতে আমার ভারি কষ্ট হয়, অথচ দাদাকেও আসল অবস্থাটা খুলে বলতে পারিনে, তাতেও কষ্ট হয়।
দাদা বাইরে এসে বললে–মাছ তো কম কেনা হয়নি, তার ওপর আবার মাঠের পুকুর থেকে মাছ এসেছিল–এত মাছ সব হারু আর ভুন্টিরা খেয়ে ফেলেচে! বাবারে, রাক্কোস সব এক-একটি! একখানা মাছও খেতে পেলাম না।
দাদাকে ভগবান এমন বোকা করে গড়েছিলেন কেন তাই ভাবি।
সীতা এ-সব বিষয়ে অত্যন্ত বুদ্ধিমতী। এই সে-দিনও তো দেখেচি সীতা রান্নাঘরে খেতে বসেচে-সামনেই জ্যাঠাইমাও খেতে বসলেন। জ্যাঠাইমাকে ভুবনের মা এক কাঁসি মাছের তরকারি দিয়ে গেল, বড় বড় দাগা মাছ আট-দশখানা তাতে–আর সীতাকে দিলে তার বরাদ্দমত একটুকরো–জ্যাঠাইমা মাছ যত পারলেন খেলেন, বাকীটা কাঁসিতেই রেখে দিলেন, সেই পাতে তাঁর ভাগ্নে-বৌ বসবে। সীতার পাতে তো একখানা মাছও নিজের পাত থেকে দিতে পারতেন। কিন্তু কই, তা নিয়ে সীতা তো কখনো কিছু বলে না, দুঃখ করে না, নালিশ করে না! আমি জানতে পারলাম এই জন্যে যে, আমি সে-সময় নিতাইকাকার জন্যে আগুন আনতে রান্নাঘরে গিয়েছিলাম-সীতা কোন কথা আমায় বলেনি। এ বাড়ির কাণ্ডই এ রকম, আজ এক বছরের ওপর তো দেখে আসছি। অবিশ্যি নিজের জন্য আমি গ্রাহ্যও করিনে, আমার দুঃখ হয় ওদের জন্যে।
মায়ের দুঃখও এ বাড়িতে কম নয়। অত খাটুনির অভ্যেস মায়ের ছিল না কোনো কালে। এই শীতকালে মাকে গোছা গোছা বাসন নিয়ে ভোরে পুকুরের জলে নামতে হয়, মা’কে আর সীতাকে। খিড়কি পুকুরের জল সকালে থাকে ঠাণ্ডা বরফ, রোদ তো পড়ে না জলে কোন কালেই, চারিধারে বড় বড় আম আর সুপুরির বাগান। এতটুকু রোদ আসে না ঘাটে, সেই কনকনে হিমজলে বসে বাসন মাজা, যেমন তেমন করে মাজলে তো এ বাড়িতে চলবে না, কোথাও দাগ থাকবার জো নেই একটু, জ্যাঠাইমা দেখে নেবেন নিজে। সে যে কি কষ্ট হয় মায়ের, মা মুখ বুজে কাজ করে যান, বলেন না কিছু, আমি তো বুঝতে পারি! ও-সব কাজ কি মা করেছেন কখনো?
সকলের চেয়ে কাজ বাড়ে পুজো-আচ্চার দিনে–এ বাড়িতে বারো মাসের বারোটা পূর্ণিমাতে নিয়মিত ভাবে সত্যনারায়ণের সিন্নি হয়। গৃহদেবতা শালগ্রামের নিত্যপূজা তো আছেই। তা ছাড়া লক্ষ্মীপূজা মাসে একটা লেগেই থাকে। এ-সব দিনে সংসারের দৈনিক বাসন বাদে পুজোর বাসন বেরোয় ঝুড়িখানেক। এঁদের সংসার অত্যন্ত সাত্বিক গোঁড়া হিন্দুর সংসার–পুজো-আচ্চার ব্যাপারে পান থেকে চুন খসবার জো নেই। সে ব্যাপারে দেখাশুনো করেন জ্যাঠাইমা স্বয়ং। ফলে ঠাকুরঘরের কাজ নিয়ে যাঁরা খাটাখাটুনি করেন, তাঁদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে ওঠে।
পুজোর বাসন যে-দিন বেরোয়, মা সে-দিন সীতাকে সঙ্গে নিয়ে যান ঘাটে। সে যতটা পারে মাকে সাহায্য করে বটে, কিন্তু একে সে ছেলেমানুষ, তাতে ও-সব কাজে তার অভ্যেস নেই একেবারেই। জ্যাঠাইমার পছন্দমত পুজোর বাসন মাজতে সক্ষম হওয়া মানে অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া–বরং বোধ হয় শেষেরটাই কিছু সহজ। জ্যাঠাইমা বলবেন,–কোষাকুষি মাজবার ছিরি কি তোমার সেজবৌ? কতদিন ব’লে দিইচি তামার পাত্তরে তেঁতুল নেবু না দিলে ম্যাড়ম্যাড় করবেই–শুধু বালি দিয়ে ঘষলে কি আর– ঠাকুরদেবতার কাজগুলোও তো একটু ছেদ্দা করে লোকে করে? সব তাতেই খিরিস্টানি–
মা জবাব খুঁজে পান না। যদি তিনি বলতে যান–না বড়দি, নেবু ঘষেই তো ঠাকুর ঘরের তামার বাসন বরাবরই–
জ্যাঠাইমা বাধা দিয়ে বলবেন,–আমার চোখে তো এখনো ঢ্যালা বেরোয়নি সেজবৌ? অম্বলতা দিয়ে বাসন মাজলে অমনি ছিরি হয় বাসনের? কাকে শেখাতে এসেচ? কি বলব, ভুবনের মা হেঁসেলের কাজ সেরে সময় করতে পারে না, নইলে বাসন-মাজা কাকে বলে–
জ্যাঠাইমা নিজের কথার প্রতিবাদ সহ্য করতে পারেন না, আর কেনই বা পারবেন, তিনিই যখন এ বাড়ির কর্ত্তী, এ বাড়ির সর্বেসর্বা পুত্রবধূরা, জায়েরা, ভাগ্নেবৌ, মাসীর দল, পিসির দল, সবাই যখন মেনে চলে–ভয় করে।
আমার ইস্কুলের পড়াটা শেষ হয়ে গেলে বাঁচি, এদের হাত থেকে উদ্ধার পেয়ে অন্য কোথাও চলে যাই তাহলে।
ভুবনের মা সকালে আমাকে ডেকে বললে, জিতু, তুমি যখন ইস্কুলে যাও, ভুবনকেও নিয়ে যেও না? ওর লেখাপড়া তো হ’ল না কিচ্ছু, আমি মাসে মাসে আট আনা মাইনে দিতে পারি, জিজ্ঞেস করে এসো তো ইস্কুলে, তাতে হয় কিনা?
আমি বললাম–দেবেন কাকীমা, ওতেই হয়ে যাবে, ওর তো নিচু ক্লাসের পড়া, আট আনায় খুব হবে।
ভুবনের মা আঁচল থেকে একটা আধুলি বের করে আমায় দিতে গেল। বললে– তাহলে নিয়ে রেখে দাও, আর আজ ভাত খাওয়ার সময়ে ভুবনকেও ডেকে খেতে বসিও। ও আমার কথা শোনে না–তুমি একবার ইস্কুলে ভুলিয়ে-ভালিয়ে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করে দিলে তারপর থেকে ভয়ে ভয়ে আপনি যাবে। মাথার ওপর কেউ নেই, বেজায় বেয়াড়া হয়ে উঠছে দিন দিন।
তার পর আমার হাত দুখানা খপ করে ধরে ফেলে মিনতির সুরে বললে, এই উবগারটুকু তোমাকে করতে হবে বাবা জিতু–আমার কেউ নেই, কাউকে বলতে পারি নে, বৌ মানুষ, কপালই না হয় পুড়েচে, কিন্তু কি বলে যার-তার সঙ্গে কথা কই বলো তো বাবা? ব’লো একটু ভুবনকে বুঝিয়ে।
এই ভুবনের মা এ বাড়িতে কি রকমে ঢুকলো, মার মুখে সে কথা আমি শুনেচি। এই গাঁয়েই ওর বাড়ি। ওর এক সতীন আছে, স্বামী মারা যাওয়ার পরে সম্পত্তির অর্ধেক ভাগ পাছে দখল করতে না পেরে ওঠে, এই ভয়ে জ্যাঠামশায়ের নামে বুঝি লেখাপড়া করে দেয়। কথা থাকে, এরা ওদের দুজনকে চিরকাল খেতে পরতে দেবে। কিন্তু এ বাড়িতে ভুবনের মা আছে চাকরানীরও অধম হয়ে। রাঁধুনীকে রাঁধুনী, চাকরানীকে চাকরানী। আর এত হেনস্থাও সবাই মিলে করে ওকে!
ভুবনের মা হয়েচে এ সংসারে অমঙ্গলের থার্মোমিটার। অর্থাৎ মঙ্গল যখন আসে, তখন ভুবনের মায়ের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্কই নেই–অমঙ্গল এলেই কিন্তু ভুবনের মায়ের দোষ। জ্যাঠাইমা অমনি বলবেন–যেদিন থেকে ও আমার বাড়ি ঢুকেছে, সেইদিন থেকেই জানি এ বাড়ির আর ভাষ্যি নেই। সাত কুল খেয়ে যে আসে, তার কি আর– তখুনি কর্তাকে বলেছিলাম ও পাপ ঢুকিও না সংসারে, কাঙালের কথা বাসি হ’লে মিষ্টি লাগে!
আমি নিজের কানে কতদিন এ ধরনের কথা শুনেচি। মা বলেন, ভুবনের মায়ের মত বোকা লোক তিনি কখনো দেখেননি।
চৈত্র মাসের গোড়ার দিকে মেজকাকার ছেলে সলিল বললে–জানো জিতুদা, মঙ্গলবারে আমাদের বাড়িতে গোপীনাথ জীউ ঠাকুর আসবেন? ও পাড়ায় মেজ-জ্যাঠামশায়দের বাড়ি ঠাকুর এখন আছেন, মঙ্গলবারে আসবেন, দু-মাস থাকবেন, তারপর আবার হরিপুরের বৃন্দাবন মুখুয্যের বাড়ি থেকে তারা নিতে আসবে। বছরে এই দু-মাস আমাদের পালা।
দাদাও সেখানে ছিল, বললে,–খুব খাওয়া-দাওয়ান হবে?
সলিল বললে–যে-দিন আসবেন, সেদিন তো গাঁয়ের সব ব্রাহ্মণের নেমন্তন্ন, তা ছাড়াও রোজ বিকেলে শেতল হবে, রাত্তিরে ভোগ–সে ভারি খাওয়ার মজা।
দাদা ও আমি দু-জনেই খুশী হয়ে উঠি। মঙ্গলবার সকাল থেকে বাড়িতে বিরাট হৈ-চৈ পড়ে গেল, ঠাকুরঘর ধোওয়া শুরু হ’ল, বাসন-কোসন কাল বিকেল থেকেই মাজাঘষা চলচে, ভুবনের মা রাত থাকতে উঠে রান্নাঘরে ঢুকেছে, পাড়ার অনেক ঝি-বউ অবিশ্যি যথেষ্ট কাজে সাহায্য করচে, একটি দল তো কাল রাত থেকে তরকারি কুটচে একরাশ।
কাকীমারা কাল বিকেল থেকে ক্ষীরের সন্দেশ ও নারকেলের নাড়ু গড়তে ব্যস্ত আছেন। ঝিটকিপোতার গোলাবাড়ি থেকে গাড়িখানেক আখ, শশা, কলা, নারকোল এসেছে, সেগুলো কাটা, ছাড়ানো ব্যাপারে বাড়ির ছোট ছোট মেয়েদের নাইয়ে ধুইয়ে দেওয়া কাপড় পরিয়ে লাগানো হয়েছে।
বাড়ির ছেলেমেয়েরা সকাল সকাল স্নান সেরে ধোয়া ধুতি-চাদর গায়ে ঠাকুর আনতে গেল কর্তাদের সঙ্গে, তাঁরাও গরদের জোড় পরে আগে আগে চলেচেন। ছেলেরা কাঁসর ঘণ্টা বাজিয়ে বেলা দশটার সময় তাঁদের সঙ্গে ঠাকুর নিয়ে ফিরলো। জ্যাঠাইমা জলের ঝারা দিতে দিতে দরজা থেকে এগিয়ে গিয়ে ঠাকুরকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে এলেন। মেয়েরা শাঁখ বাজাতে লাগলেন। ধূপধুনোর ধোঁয়ায় ঠাকুরঘরের বারান্দা অন্ধকার হয়ে গেল। আমি এ-দৃশ্য কখনো দেখিনি–আমার ভারি আনন্দ হ’ল, ইচ্ছে হ’ল আর একটু এগিয়ে গিয়ে ঠাকুরঘরের দোরে দাঁড়িয়ে দেখি, কিন্তু ভয় হ’ল পাছে জ্যাঠাইমা বকুনি দেন, বলেন–তুই এখানে দাঁড়িয়ে কেন? কি কাপড়ে আছিস তার নেই ঠিক, যা সরে যা।
এমন অনেকবার বলেচেন–তাই ভয় হয়।
বেলা একটা পর্যন্ত আমাদের পেটে কিছু গেল না। বাড়ির অন্যান্য ছেলেমেয়েদের কথা স্বতন্ত্র–তাদেরই বাড়ি, তাদেই ঘরদোর। তারা যেখানে যেতে পারে, আমরা তিন ভাইবোনেই লাজুক, সেখানে আমরা যেতে সাহস করি না, কারুর কাছে খাবার চেয়েও খেতে পারিনে। মা ব্যস্ত আছেন নানা কাজে, অবিশ্যি হেঁসেলের কাজে তাঁকে লাগানো হয় না এ বাড়িতে, তা আমি জানি। কিন্তু ঝিয়ের কাজ করতে তো দোষ নেই! বাড়ির অন্যান্য মেয়েরা কোনদিনই আমাদের খাওয়াদাওয়ার খোঁজ করেন না, আজ তো সকলেই মহাব্যস্ত।
বেলা যখন দেড়টা আন্দাজ, রান্নাঘরের দিকে একটা গোলমাল ও জ্যাঠাইমার গলার চীৎকার শুনে ব্যাপার কি দেখতে গেলাম ছুটে। গিয়ে দেখি, রান্নাঘরের কোণে ছেঁচতলার কাছে দাদা একটা লাউপাতা হাতে দাঁড়িয়ে। জ্যাঠাইমা বকচেন–ওই ঝাড় তো, আর কত ভাল হবে তোমাদের? এখনো বামুন-ভোজন হ’ল না, দেবতার ভোগ রইল পড়ে, উনি এসেছেন ভোগের আগে পেরসাদ পেতে,–দেবতা নেই, বামুন নেই, ওর শুয়োর-পেট পোরালেই আমার স্বগগে ঘণ্টা বাজবে যে! বুড়ো দামড়া কোথাকার–ও-সব খিরিস্টান চাল এ বাড়িতে চলবে না বোলে দিচ্ছি, মুড়ো ঝাঁটা মেরে বাড়ি থেকে বিদেয় করে দেবো জানো না? আমার বাড়ি বসে ও-সব অনাচার হবার জো নেই, যখন করে তখন করেচ।
মা কোথায় ছিলেন আমি জানিনে। পাছে তিনি শুনতে পান এই ভয়ে দাদাকে আমি সঙ্গে করে বাইরে নিয়ে এলাম। দাদা লাউপাতাটা হাতে নিয়েই বাইরে চলে এল। আমি বললাম–ওখানে কি কচ্ছিলে?
দাদা বললে–কি আবার করবো? ভুবনের মা কাকীমার কাছে দুখানা তিলপিটুলি ভাজা চাইছিলাম–বড় খিদে পেয়েছে তাই। জ্যাঠাইমা শুনতে পেয়ে কি বকুনিটাই–
ব’লেই লজ্জা ও অপমান ঢাকবার চেষ্টায় কেমন এক ধরনের হাসলে। হয়তো বাড়ির কোনো ছেলেই এখনো খায়নি, কিন্তু আমরা জানি দাদা খিদে মোটে সহ্য করতে পারে না, চা-বাগানে থাকতে ভাত নামতে-না-নামতে সকলের আগে ও পিঁড়ি পেতে রান্নাঘরে খেতে বসে যেত। বয়সে বড় হলে কি হবে, ও আমাদের সকলের চেয়ে ছেলেমানুষ।
আজকার সমস্ত অনুষ্ঠানের উপর আমার বিতৃষ্ণা হ’ল। এদের দয়ামায়া নেই, এই যে ঠাকুর-পুজোর ধুমধাম, এর যেন কোথায় গলদ আছে। কোথায়–তা বোঝা আমার বুদ্ধিতে কুলোয় না, কিন্তু গোটা ব্যাপারটাই যেন কেমন মনের সঙ্গে খাপ খেলো না আদৌ।
আর কিছুদিন পরে একটু বয়স হলে আমি বুঝেছিলাম যে, এদের ভক্তির উৎসের মূলে এদের বিষয়-বুদ্ধি ও সাংসারিক উন্নতি। ভগবান এদের উন্নতি করচেন, ফসল বাড়াচ্চেন, মান-খাতির বাড়াচ্চেন–এঁরাও ভগবানকে খুব তোয়াজ করচেন–ভবিষ্যতে আরও যাতে বাড়ে। প্রতি পূর্ণিমায় ঘরে সত্যনারায়ণ পুজো হয়, সংক্রান্তিতে-সংক্রান্তিতে দুটি ব্রাহ্মণ খাওয়ানো হয়, শুধু তাই নয়–একটি গরিব ছাত্রকে জ্যাঠাইমা বছরে একটি টাকা দিয়ে থাকেন বই কেনার জন্যে। শ্রাবণ মাসে তাঁদের আবাদ থেকে বছরের ধান, জালাভরা কই মাছ, বাজরাভরা হাঁসের ডিম, তিল, আকের গুড়, আরও অনেক জিনিস নৌকা বোঝাই হয়ে আসতো। ভক্তিতে আপ্লুত হয়ে তাঁরা প্রতিবার এই সময় পাঁঠাবলি দিয়ে মনসাপুজো করতেন ও গ্রামের ব্রাহ্মণদের খাওয়াতেন। এদের সত্যনারায়ণ পুজো ঘরের সচ্ছলতা বৃদ্ধি করার জন্যে, লক্ষ্মীপুজো ধনধান্য বৃদ্ধির জন্যে, গৃহ-দেবতার পুজো, গোপীনাথ জীউর পুজো–সবারই মূলে–হে ঠাকুর, ধনেপুত্রে যেন লক্ষ্মীলাভ হয় অর্থাৎ তা হ’লে তোমাকেও খুশী রাখবো।
বাবার মুখে শুনেচি, এ সমস্ত বাড়িঘর আমার ঠাকুরদাদা গোবিন্দলাল মুখুয্যের তৈরি। ঠাকুরদাদা যখন মারা যান, বাবার তখন বয়স বেশী নয়। তিনি মামার বাড়িতে মানুষ হন এবং তারপর চাকরি নিয়ে বিদেশে বার হয়ে যান। জ্যাঠামশাইয়ের বাবা নন্দলাল মুখুয্যে নায়েবী কাজে বিস্তর পয়সা রোজগার করেছিলেন এবং আবাদ অঞ্চলে একশো বিঘে ধানের জমি কিনে রেখে যান। আবাদ-অঞ্চল মানে কি, আমি এতদিনেও জানতাম না, এই সেদিন জ্যাঠামশাইদের আড়তের মুহুরী যদু বিশ্বাসকে জিজ্ঞেস করে জেনেছি।
জ্যাঠামশাই পাটের ব্যবসা করে খুব উন্নতি করেছেন। এঁদের বর্তমান উন্নতির মূলেই এঁদের পাটের ও ধানের কারবার। জ্যাঠামশাইরা তিন ভাই–সবাই এই আড়তের কাজেই লেগে আছেন দেখতে পাই। এঁরা বাবার খুড়তুতো ভাই, বাবাই ঠাকুরদাদার একমাত্র ছেলে ছিলেন। বাবা কোনোকালেই এ-গাঁয়ে বাস করেননি, জমিজমা যা ছিল তাও এখন আর নেই, বাবা বেঁচে থাকতে জ্যাঠামশাইকে বলতে শুনেছিলাম যে, সব নাকি রোডসেস নীলামে বিক্রি হয়ে গেছে। সে-সব কি ব্যাপার যত বুঝি আর না বুঝি, এটুকু আজকাল বুঝেছি যে, এখানে আমাদের দাবি কিছু নেই এবং জ্যাঠামশাইদের দয়ায় তাঁদের সংসারে মাথা গুঁজে আমরা আছি।
জ্যাঠাইমাকে আমার নতুন নতুন ভারি ভাল লাগতো, কিন্তু এতদিন আমরা এ বাড়িতে এসেচি, একদিনের জন্যও আমাদের সঙ্গে তিনি ভাল ব্যবহার করেননি–আমাকে ও দাদাকে তো নখে ফেলে কাটেন এমনি অবস্থা। অনবরত জ্যাঠাইমার কাছ থেকে গালমন্দ অপমান খেয়ে খেয়ে আমারও মন বিরূপ হয়ে উঠেছে। আজকাল আমি তো জ্যাঠাইমাকে এড়িয়ে চলি, সীতাও তাই, দাদা ভালমন্দ কিছু তেমন বোঝে না, ও নবান্নের দিন বাটি হাতে জ্যাঠাইমায়ের কাছে নবান্ন চাইতে গিয়ে বকুনি খেয়ে ফিরে আসবে–পুকুরের ঘাটে নাকি জ্যাঠাইমা নেয়ে উঠে আসছিলেন, ও সে-সময় ঝাঁপিয়ে জলে পড়ার দরুন জল ছিটিয়ে তাঁর গায়ে লাগে, সেজন্য মার খাবে–বাসি কাপড়ে জ্যাঠাইমার ঘরে ঢুকে এই সেদিনও মার খেতে খেতে বেঁচে গিয়েছে। কেন বাপু যাওয়া?
কিন্তু না গেলেই যে বিপদের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায় তা নয়, এক সংসারে থাকতে গেলে ছোঁয়াছুঁয়ি ঠেকাঠেকি না হয়ে তো পারে না, অথচ হ’লেই আর রক্ষে নেই।
জ্যাঠাইমাদের রোয়াকে বসে আমি আর ভুবন খেলছি–এমন সময় জ্যাঠাইমা ওপরের দালান থেকে ঝিন্টু, বাদল, ঊষা, কাতু–ওদের ডাক দিলেন। ডাকলেন কেন, আমি তা জানি, খাবার খাওয়ার জন্যে–আমি আর ভুবন যে সেখানে আছি, তা দেখেও দেখলেন না। আমি ভুবনকে বসতে বলে মায়ের কাছ থেকে বড় এক বাটি মুড়ি নিয়ে এসে দু’জনে খেতে লাগলাম। কাতু ফিরে এলে বললাম–ভাই, এক ঘটি জল নিয়ে আয় না খাবো! খাবার খাওয়া সেরে আমরা আবার খেলা করছি, এমন সময়ে জ্যাঠাইমা সেখানে এলেন কাপড় তুলতে। রোয়াকের ধারে আমাদের মুড়ির বাটিটার দিকে চেয়ে বললেন–এ বাটিতে হাত ধুয়েচে কে? এ ঠিক জিতুর কাজ, নইলে অমন মেলেচ্ছো এ বাড়ির মধ্যে তো আর কেউ নেই।
কি করে ফেলেছি না জানি! ভয়ে ভয়ে বললাম–কি হয়েচে জ্যাঠাইমা?
জ্যাঠাইমা মারমুখী হয়ে বললেন–কি হয়েচে দেখতে পাচ্ছো না? দুকুরবেলা কাপড়খানা কেচে আলনায় রেখে গিইচি, কাচা কাপড়খানা জল ছিটিয়ে এঁটো ক’রে বসে আছো?
মেজকাকীমার এক পিসী না মাসী এ বাড়িতে থাকে, বুড়ী ভারি ঝগড়াটে আর জ্যাঠাইমা খোশামুদে। বয়স পঞ্চাশ ষাট হবে, কালো, একহারা দড়িপাকানো গড়ন–সীতা আর আমি আড়ালে বলি–তাড়কা রাক্কুসী। নানা ছুতোনাতায় মাকে অনেকবার বকুনি খাইয়েচে জ্যাঠাইমা-কাকীমাদের কাছে। ওকে দু-চক্ষে আমরা দেখতে পারিনে। জ্যাঠাইমার গলার স্বর শুনে রান্নাঘরের উঠোন থেকে বুড়ী ছুটে এল।–কি হয়েচে বৌমা, কি হয়েছে?
জ্যাঠাইমা বললেন–সন্দেবেলা আহ্নিক করবো বলে কাপড়খানা কেচে আলনায় দিয়ে রেখেচি মাসী–আর বুড়োধাড়ী ছোঁড়া করেচে কি, এখেনে মুড়ি খেয়ে সেই বাটিতেই জল দিয়ে হাত ধুয়েচে, আর এই রোয়াকের ধারেই তো কাপড়–তুমি কি বলতে চাও কাপড়ে লাগেনি জলের ছিটে?
বুড়ী অবাক হবার ভান করে বলে–ওমা সে কি কথা! লাগেনি আবার, একশো বার লেগেছে।
আমি ভাবলাম, বারে! এতে আর হয়েছে কি? জল যদি লেগেই থাকে, দু-চার ফোঁটা লেগেচে বই তো নয়? জ্যাঠাইমাকে বললাম–জল তো ওতে লাগেনি জ্যাঠাইমা, আর যদিও একটু লেগে থাকে, এখনও রোদ রয়েছে, এক্ষুনি শুকিয়ে যাবে’খন।
বুড়ী বললে–শোনো কথা ও ছোঁড়ার জ্ঞান-কাণ্ড একেবারেই নেই–একেবারে মেলেচ্ছো–ওর মাও তাই। হিঁদুয়ানি তো শেখেনি কোনোদিন–
–তোমরা শোন মাসী, আমি শুনে শুনে হদ্দ হয়ে গিয়েছি। ঘরে ঠাকুর রয়েছেন, আর এই সব অনাচার কি করে বরদাস্ত করি বল তো তুমি? আমার কোনো ছেলেমেয়ে ওরকম করবে? অত বড় ধাড়ী ছেলে হ’ল, মুড়ির বাটিতে জল ঢাললে যে সকড়ি হয় সেও জানে না! শুনবে কোথা থেকে, মেলেচ্ছো খিরিস্টানের মধ্যে এতকাল কাটিয়ে এসেছে, ভালো শিক্ষে দিয়েচে কে? হিঁদুর বাড়িতে কি এ সব পোষায়? বল তো তুমি—
বুড়ী বললে–ওর মা জানে না তা ও জানবে কোথা থেকে? সেদিন ওর মা করেচে কি, পুকুরঘাটে তো বড় নৈবিদ্যির বারকোশখানা ধুতে নিয়ে গিয়েছে–যেদিন ঠাকুর এলেন বুড়ী দু-হাত জোড় করে নমস্কার করলে তার পরের দিন–আমি দাঁড়িয়ে ঘাটে, কাপড় কেচে যখন উঠলি তখন ধোওয়া বারকোশখানা আর একবার জলে ডুবো–না ডুবিয়েই অমনি উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমি দেখে বলি, ও কি কাণ্ড বউ? ভাগ্যিস দেখে ফেললাম তাই তো–
মায়ের দোষ দেওয়াতেই হোক, বা আমাকে আগের ওই-সব কথা বলাতেই হোক, আমার রাগ হ’ল। তা ছাড়া আমার মন বললে এতে কোন দোষ হয়নি–মুড়ির বাটিতে জল ঢালার দরুনে মুড়ির বাটি অপবিত্র হবে কেন? মা বারকোশ ধুয়ে জলের ধারে রেখে স্নান সেরে উঠে যদি সে বারকোশ নিয়ে এসে থাকেন, তাতে মা কোন অন্যায় কাজ করেননি। বললাম–ওতে দোষ কি জ্যাঠাইমা, মুড়িও খাবার জিনিস, জলও খাবার জিনিস–দুটোতে মেশালে খারাপ হবে কেন, ছুঁতে থাকবেই বা না কেন?
জ্যাঠাইমা অগ্নিমূর্তি হয়ে উঠলেন–তোর কাছে শাস্তর শুনতে আসিনি, ফাজিল ছোঁড়া কোথাকার–তোরা তো খিরিস্টান, হিঁদুর আচারব্যাভার তোরা জানিস কি, তোর মা-ই বা জানে কি? ওইটুকু ছেলে গলা টিপলে দুধ বেরোয়, উনি আবার আমায় শাস্তর বোঝাতে আসেন! শিখবি কোত্থেকে, তোর মা তোদের কি কিছু শিখিয়েচে, না কিছু জানে? পয়সা রোজগার করেছে আর দু-হাতে উড়িয়েচে তোর বাবা-মদ খেয়ে খিরিস্টানি কোরে–
বুড়ী বললে–মোলোও সেই রকম। যেমন-যেমন কম্মফল তেমন-তেমন মিত্যু! দশেধম্মে দেখলে সবাই, যে কম্মের যে শাস্তি–ঘর থেকে মড়া বেরোয় না, ও-পাড়ার হরিদাস না এসে পড়লে ঘরের মধ্যেই পড়ে থাকতো–
বাবার মৃত্যু সম্পর্কে এ কথা বলাতে আমার রাগ হ’ল। মরণের পরে এখনো তাঁর কথা ভেবে আমার কষ্ট হয়, যদিও সে কথা কাউকে বলিনে। বললাম–ভাল মরণ আর মন্দ মরণ নিয়ে বাহাদুরি কি দিদিমা? এই তো মাঘ মাসে ওই তেঁতুলতলায় যাদের বাড়ি, ওই বাড়ির সেই বুড়ো গাঙ্গুলীমশায় মারা গেলেন, তিনি তো ভালমানুষ ছিলেন সবাই বলে, পুকুরের ঘাটে এক বেলা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আহ্নিক করতেন, তবে তিনি পেনসন আনতে গিয়ে ও-রকম করে সেখানে মারা গেলেন কেন? সেখানে কে তাঁর মুখে জল দিয়েছে, কে মড়া ছুঁয়েছে, কোথায় ছিল ছেলেমেয়ে, ও-রকম হ’ল কেন?
আমার বোকামি, আমি ভেবেছিলাম ঠিকমত যুক্তি দেখিয়ে বুড়ীকে তর্কে হারাবো, কিন্তু তার ধরনের ঝগড়ায় মজবুত পাড়াগাঁয়ের মেয়ে যে অত সহজে হার মেনে নেবে, এ ধারণা করাই আমার ভুল হয়েছিল। সে যুক্তির পথে গেলই না।
–মরুক বুড়ো গাঙ্গুলী, তবুও খবর পেয়ে তার ছেলেজামাই গিয়ে তাকে এনে গঙ্গায় দিয়েছিল, তোর বাবার মত দোগেছের মাঠে ডোবার জলে আধ-পোড়া করে ফেলে রেখে আসেনি! আমি সব জানি, আমায় ঘাঁটাসনে, অনেক আদ্যিনাড়ির কথা বেরিয়ে যাবে। কাঠ জোটেনি খেজুরের ডাল দিয়ে পুড়িয়েছিল, সব শুনিচি আমি। দোগেছের মাঠে সন্দের পর লোক যায় না, সবাই বলে এখনও ভূত হয়ে–
কথা সবই সত্যি, শেষেরটুকু ছাড়া। ঐটুকুর ওপরই জোর দিয়ে বললাম–মিথ্যে কথা, বাবা কখখনো,–তার যুক্তির অকাট্যতা প্রমাণ করবার জন্যে এমন একটা কথা বলে ফেললাম যা কখনো কারুর কাছে বলিনি বা খুব রেগে মরীয়া না হয়ে উঠলে বলতামও না এদের কাছে। বললাম–জানেন, আমি ভূত দেখতে পাই, অনেক দেখেচি, বাবাকে তা হলে নিশ্চয়ই দেখতে পেতাম, জানেন? চা-বাগানে থাকতে আমি কত–
এই পর্যন্ত বলেই আমি চুপ করে গেলাম। দিদিমা খিল খিল করে হেসেই খুন।–হি হি, এ ছোঁড়াও পাগল ওর বাপের মত–হি হি-শুনেচো বউমা, হি হি–কি বলে শুনেছো একবার–
জ্যাঠাইমা বললেন–যা এখান থেকে এই মুড়ির বাটি তুলে ধুয়ে নিয়ে আয় পুকুর থেকে, এখানটা গায়ের জল দিয়ে ধুয়ে দে। আমার কাপড়খানাও কেচে নিয়ে আয় অমনি, তোর সঙ্গে কে এখন সন্দে অবধি তক্কো করে? তবে বলে দিচ্ছি, হিঁদুর ঘরে হিঁদুর মত ব্যাভার না করলে এ বাড়িতে জায়গা হবে না। পষ্ট কথায় কষ্ট নেই। কই আমাদের বুলু, ভুন্টি, হাবু কি সতীশ তো কখনো এমন করে না, যা বলি তখুনি তাই তো শোনে, কই এক দিনের জন্যেও তো—
দিদিমা বললেন–ওমা বুলু, হাবু, সতীশের কথা বলো না, তারা আমার বেঁচে থাক, সোনার চাঁদ ছেলেমেয়ে সব। তারা হিন্দুয়ানির যা জানে ওর মা তা জানে না তো ও! সে দিন সতীশকে বলচি, সতু দাদাভাই, তেলের ভাঁড়টা বাইরের উঠোনে নিমু কলুকে দিয়ে এসো তো? তো বলচে–আমার বিছানার কাপড়, আমি তো ভাঁড় ছোঁব না। আমি মনে মনে ভাবলাম, দ্যাখো শিক্ষের গুণ দ্যাখো–কেমন ঘরে মানুষ তারা। আহা বেঁচে থাক– সব বেঁচে থাক–
মনে মনে সতীশের প্রশংসা করতে চেষ্টা করলাম। সতীশ যে স্বীকার করেছে তার কাপড় বাসি, এটা অবিশ্যি প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু বাসি কাপড়ে কিছু ছোঁয়া যে খারাপ কাজ, এ বিশ্বাস যার নেই, তাকেই বা দোষ দেওয়া যায় কি করে, এ আমি বুঝতে পারিনে। যেমন এখনই আমার মনে একটা প্রশ্ন এসেছে যে, নিমু কলু কি কাচা, ধোয়া, শুদ্ধ গরদের জোড় প’রে তেল বেচতে এসেছিল? সতীশের ভেবে দেখবার ক্ষমতা ও বুদ্ধির চেয়ে যদি কারুর বুদ্ধি ও বুঝবার শক্তি বেশী থাকে, তার জন্যে তাকে কি নরকে পচে মরতে হবে?
.
০২.
তিন বছর এখনও হয়নি, আমরা এ গাঁয়ে এসেছি। তার আগে ছিলাম কার্সিয়াঙের কাছে একটা চা-বাগানে, বাবা সেখানে চাকরি করতেন। সেখানেই আমি ও সীতা জন্মেছি, কেবল দাদা নয়, দাদা জন্মেছে হনুমান-নগরে, বাবা তখন সেখানে রেলে কাজ করতেন। সেখানেই আমরা বড় হয়েছি, এখানে আসবার আগে এত বড় সমতলভূমি কখনো দেখিনি। আমরা জানতাম চা-ঝোপ, ওক আর পাইনের বন, ধুরা গাছের বন, পাহাড়ী ডালিয়ার বন, ঝর্ণা, কনকনে শীত, দূরে বরফে ঢাকা বড় বড় পাহাড়-পর্বতের চূড়া, মেঘ, কুয়াশা, বৃষ্টি। এখানে প্রায়ই মাঝে মাঝে চা-বাগানের কথা, আমাদের নেপালী চাকর থাপার কথা, উমপ্লাঙের ডাক-রানার খড়্গ সিং যে আমাদের বাংলোতে মাঝে মাঝে ভাত খেতে আসতো–তার কথা, মিস নর্টনের কথা, পচাং বাগানের মাসীমার কথা, আমাদের বাগানের নীচের সেই অদ্ভুত রাস্তাটার কথা, মনে হয়।
সেই সব দিনই আমাদের সুখে কেটেচে। দুঃখের শুরু হয়েছে যে-দিন বাংলা দেশে পা দিয়েছি। এই জন্যে এই তিন বছরেও বাংলা দেশকে ভাল লাগলো না–মন ছুটে যায় আবার সেই সব জায়গায়, চা-বাগানে, শেওলা-ঝোলা বড় বড় ওকের বনে, উমপ্লাঙের মিশন হাউসের মাঠে–যেখানে আমি, সীতা, দাদা কতদিন সকালে ফুল তুলতে যেতাম, বড়দিনের সময় ছবির কার্ড আনতে যেতাম, কেমন মিষ্টি কথা বলতে ভালবাসতো মিস নর্টন। ভাবতে বসলে এক একটা দিনের কথা এমন চমৎকার মনে আসে!…
শীতের সকাল।
বাড়ির বার হয়েই দেখি চারিধারে বনে জঙ্গলে পাহাড়ের ঢালুর গায়ে পাইন গাছের ফাঁকে বেশ রোদ। আমি উঠতাম খুব সকালেই, সীতা ও দাদা তখন লেপের তলায়, চা না পেলে এই হাড়কাঁপানো শীতে উঠতে কেউ রাজী নয়।
শীতও পড়েছে দস্তুরমত। আমাদের বাগানের দক্ষিণে কিছু দূরে যে বড় চা-বাগানটা নতুন হয়েছে, যার বাংলোগুলোর লাল টালির ঢালু ছাদ আমাদের এখান থেকে দেখা যায় পাইন গাছের ফাঁকে, আজ তাদের লোকজনেরা চায়ের চারাগাছ খড়ের পালুটি দিয়ে ঢেকে দিচ্ছে বোধ হয় বরফ পড়বার ভয়ে। আকাশ পরিষ্কার, সুনীল, কোনোদিকে এতটুকু কুয়াশা নেই বরফ পড়বার দিন বটে।
একটু পরে সীতা উঠল। সে রোগা, ফর্সা, ছিপছিপে। সে ও দাদা খুব ফর্সা, তবে অত ছিপছিপে আর কেউ নয়। সীতা বললে, থাপা কোথায় গেল দাদা? আজ ও সোনাদা যাবে? বাজার থেকে একটা জিনিস আনতে দেবো।
আমি বললাম–কি জিনিস রে?
সীতা দুষ্টুমির হাসি হেসে বললে, বলবো কেন? তোমরা যে কত জিনিস আনাও, আমায় বলো?
একটু পরে থাপা এল। সে হপ্তায় দু-দিন সোনাদা বাজারে যায় তরকারি আর মাংস আনতে। সীতা চুপি চুপি তাকে কি আনতে বলে দিলে, আড়ালে থাপাকে জিজ্ঞেস করে জানলাম জিনিসটা একপাতা সেফটিপিন। এর জন্যে এতো!
একটু বেলায় বরফ পড়তে শুরু হ’ল। দেখতে দেখতে বাড়ির ছাদ, গাছপালার মাথা, পথঘাট যেন নরম থোকা থোকা পেঁজা কাপাস তুলোতে ঢেকে গেল। এই সময়টা ভারি ভাল লাগে, আগুনের আংটাতে গনগনে আগুন–হাড়কাঁপানো শীতের মধ্যে আগুনের চারিধারে বসে আমি দাদা ও সীতা লুডো খেলতে শুরু করে দিলাম।
এই সময় বাবা এলেন আপিস থেকে। ম্যানেজারের কুঠীর পাশেই আপিস-ঘর, আমাদের বাংলো থেকে প্রায় মাইলখানেক, কি তার একটু বেশী। বাবা বেলা এগারোটার সময় ফিরে খাওয়া-দাওয়া করে একটু বিশ্রাম করেন, তিনটের পরে বেরোন, ওদিকে রাত আটটা-ন’টায় আসেন।
বাবা আমাদের সকলকে নিয়ে খেতে ভালবাসেন। সীতাকে ডেকে বললেন–খুকী থাপাকে বলে দে নাইবার জন্যে জল গরম করতে–আর তোরা সব আজ আমার সঙ্গে খাবি–নিতুকে বলিস নইলে সে আগেই খাবে।
মা রান্নাঘরে ব্যস্ত ছিলেন। সীতা গিয়ে বললে–মা, দাদাকে আগে ভাত দিও না, আমরা সবাই বাবার সঙ্গে খাবো।
সীতার কথা শেষ হতে না হতে দাদা গিয়ে রান্নাঘরে হাজির। দাদা খিদে মোটে সহ্য করতে পারে না–তাই আমাদের সকলের আগে মা তাকে খেতে দিতেন। এদিকে আমাদের ক’ ভাই-বোনের মধ্যে বাবা সকলের চেয়ে ভালবাসতেন দাদাকে ও সীতাকে। দাদাকে খাওয়ার সময়ে কাছে বসে না খেতে দেখলে তিনি কেমন একটু নিরাশ হতেন, যেন অনেকক্ষণ ধরে যেটা চাইছিলেন সেটা হ’ল না।
সীতা বললে–দাদা তুমি খেও না, বাবা আজ সকলকে নিয়ে খাবেন। বাবা নাইচেন, এক্ষুনি আমরা খেতে বসবো–
দাদা কড়া থেকে মাকে একটুকরো মাংস তুলে দিতে বললে এবং গরম টুকরোটা মুখে পুরে দিয়ে আবার তখুনি তাড়াতাড়ি বার করে ফেলে বার-দুই ফুঁ দিয়ে আবার মুখে পুরে নাচতে নাচতে চলে গেল। দাদাকে আমরা সবাই খুব ভালবাসি, দাদা বয়সে সকলের চেয়ে বড় হলেও এখনো সকলের চেয়ে ছেলেমানুষ। ও সকলের আগে খাবে, সকলের আগে ঘুমিয়ে পড়বে। ঘুরিয়ে কথা বললে বুঝবে না, অন্ধকারে একলা ঘরে শুতে পারবে না–ওর বয়স যদিও বছর চোদ্দ হ’ল, কিন্তু এখনও আমাদের চেয়ে ও ছেলেমানুষ, প্রথম সন্তান ব’লে বাপ-মায়ের বেশী আদর ওরই ওপর।
আমরা সবাই একসঙ্গে খেতে বসলাম। বাবা সীতাকে একপাশে ও দাদাকে আর একপাশে নিয়ে খেতে বসেছেন। মাংসের বাটি থেকে বাবা চর্বি বেছে বেছে ফেলে দিতেই সীতা বললে–বাবা আমি খাবো—
দাদা বললে–তুই সব খাসনে, আমাকে দু’খানা দে সীতা–
বাবা অত চর্বি ওদের খেতে দিলেন না। ওদের এক এক টুকরো দিয়ে বাকি টুকরোগুলো বেড়ালদের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। আমায় বললেন–জিতু, গায়ের মাপটা দিস তো তোর, ওবেলা সায়েবের দর্জি আসবে, তার কাছে তোর জামা করতে দেবো–
সীতা বললে–আমার আর একটা জামা কার বাবা—
তবে তুইও দিস গায়ের মাপটা,–ওই সঙ্গেই দিস–
মা বললেন–তার দরকার কি, তুমি তাকে বাসায় পাঠিয়ে দিও না। আমি সব দেখেশুনে দেবো–আরও করবার জিনিস রয়েচে–নিতুর মোটে দুটো জামা, ওর ওভারকোটটা পুরনো হয়ে ছিঁড়ে গিয়েছে–যেমন শীত পড়েছে এবার, ওর একটা ওভারকোট করে দাও–
বিকেলে মেমেরা মাকে পড়াতে এল।
মাইল দুই দূরে মিশনারীদের একটা আড্ডা আছে। আমি একবার মেমসাহেবের সঙ্গে সেখানে গিয়েছিলাম। সেখান থেকে খোসালডি চা-বাগানে যে রাস্তাটা পাহাড়ের ঢালু বেয়ে নেমেছে–তারই ধারে ওদের বাংলো। অনেকগুলো লাল টালির ছোট বড় ঘর, বাঁশের জাফরির বেড়ায় ঘেরা কম্পাউন্ড, এই শীতকালে অজস্র ডালিয়া ফোটে, বড় বড় ম্যাগনোলিয়া গাছ। আমাদের বাগানে ও বড় সাহেবের বাংলোতে ম্যাগনোলিয়া গাছ আছে।
এরা মাকে পড়ায়, সীতাকেও পড়ায়। মিস নর্টন দিনাজপুরে ছিল, বেশ বাংলা বলতে পারে। নানা ধরনের ছবিওয়ালা কার্ড, লাল সবুজ রঙের ছোট ছোট ছাপানো কাগজ, তাতে অনেক মজার গল্প থাকে। দাদার পড়াশুনোয় তত ঝোঁক নেই, আমি ও সীতা পড়ি। একবার একখানা বই দিয়েছিল–একটা গল্পের বই—‘সুবর্ণবণিক পুত্র’। এ কথায় আমি বুঝেছিলাম বণিকপুত্র সোনা দিয়ে গড়া অর্থাৎ সোনার মত ভালো। পাপের পথ থেকে উক্ত বণিকপুত্র কি করে ফিরে এসে খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করলে, তারই গল্প। অনেক কথা বুঝতে পারতাম না, কিন্তু বইখানা এমন ভাল লাগতো!…
মেম আসতো দু-জন। একজনের বয়স বেশী–মায়ের চেয়েও বেশী। আর একজনের বয়স খুব কম। অল্পবয়সী মেমটির নাম মিস নর্টন–একে আমার খুব ভাল লাগতো– নীল চোখ, সোনালী চুল, আমার কাছে মিস নর্টনের মুখ এত সুন্দর লাগতো, বার বার ওর মুখের দিকে চাইতে ইচ্ছে করত, কিন্তু কেমন লজ্জা হ’ত–ভালো করে চাইতে পারতাম না–অনেক সময় সে অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে থাকবার সময় লুকিয়ে এক চমক দেখে নিতাম। তখনি ভয় হ’ত হয়ত সীতা দেখছে–সীতা হয়ত এ নিয়ে ঠাট্টা করবে। ওরা আসতো বুধবারে ও শনিবারে। সপ্তাহের অন্যদিনগুলো যেন কাটতে চাইত না, দিন গুনতাম কবে বুধবার আসবে, কবে শনিবার হবে। মিস নর্টনের মত সুন্দরী মেয়ে আমি কখনো দেখিনি—-আমার এই এগারো-বারো বছরের জীবনে।
কিন্তু মাঝে মাঝে এমনি হতাশ হ’তে হ’ত! দিন গুনে গুনে বুধবার এল, কিন্তু প্রৌঢ়া মেমটি হয়তো সেদিন এল একা, সঙ্গে মিস নর্টন নেই–সারা দিনটা বিস্বাদ হয়ে যেতো, মিস নর্টনের ওপর মনে মনে অভিমান হ’ত, অথচ কেন আজ মিস নর্টন এল না সে কথা কাউকে জিজ্ঞেস করতে লজ্জা হত।
মেমেরা এক-একদিন আমাদের ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে শেখাতো। মা তখন থাকতেন না। আমি, সীতা ও দাদা চোখ বুজতাম–মিস নর্টন ও তার সঙ্গিনী চোখ বুজতো। ‘হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা সদাপ্রভু’–সবাই একসঙ্গে গম্ভীর সুরে আরম্ভ করলুম। হঠাৎ চোখ চেয়ে দেখতুম সবাই চোখ বুজে আছে, কেবল সীতা চোখ খুলে একবার জিব বার করেই আমার দিকে চেয়ে একটু দুষ্টুমির হাসি হাসলে–পরক্ষণেই আবার প্রার্থনায় যোগ দিলে।
সীতা ঐ রকম, ও কিছু মানে না, নিজের খেয়াল-খুশীতে থাকে, যাকে পছন্দ করবে তাকে খুবই পছন্দ করবে, আবার যাকে দেখতে পারবে না তার কিছুই ভাল দেখবে না। ওর সাহসও খুব, দাদা যা করতে সাহস করে না, এমন কি আমিও যা অনেক সময় করতে ইতস্তত করি–ও তা নির্বিচারে করে। আমাদের বাংলো থেকে খানিকটা দূরে বনের মধ্যে একটা দেবস্থান আছে–পাহাড়ীদের ঠাকুর থাকে। একটা বড় সরল গাছের তলায় কতকগুলো পাথর–ওরা সেখানে মুরগী বলি দেয়, ঢাক বাজায়। সবাই বলে ওখানে ভূত আছে, জায়গাটা যেমন অন্ধকার তেমনি নির্জন–একবার দাদা তর্ক তুলে বললে আমরা কখনোই ওখানে একা যেতে পারবো না। সন্ধ্যা হওয়ার আগেই সীতা বাংলোর বার হয়ে চলে গেল একাই–কোনো উত্তর না দিয়েই ছুট দিলে পাহাড়ীদের সেই নির্জন ঠাকুরতলার দিকে …ওই রকম ওর মেজাজ …
মিস নর্টন সীতাকে খুব ভালবাসে। মাঝে মাঝে সীতাকে সঙ্গে নিয়ে যায় ওদের মিশন বাড়িতে, ওকে ছবির বই, পুতুল, কেক, বিস্কুট কত কি দেয়—-ছবি আঁকতে শেখায়, বুনতে শেখায়–এরই মধ্যে সীতা বেশ পশমের ফুল তুলতে পারে, মানুষের মুখ, কুকুর আঁকতে পারে। ওরা আমাকেও অনেক বই দিয়েচে–মথি-লিখিত সুসমাচার, লুক-লিখিত সুসমাচার, যোহন-লিখিত সুসমাচার, সদাপ্রভুর কাহিনী–আরো অনেক সব। যীশু একটুকরো মাছ ও আধখানা রুটিতে হাজার লোককে ভোজন করালেন–গল্পটা পড়ে একবার আমার হঠাৎ মাছ ও রুটি খাবার সাধ হ’ল। কিন্তু মাছ এখানে মেলে না–মা ভরসা দিলেন খাওয়াবেন, কিন্তু দু মাসের মধ্যেও সেবার মাছ পাওয়া গেল না, আমার শখও ক্রমে ক্রমে উবে গেল।
বাবার বন্ধু দু-একজন বাঙালী মাঝে মাঝে আমাদের এখানে এসে দু-একদিন থাকেন। মেমেরা মাকে পড়াতে আসে, এ ব্যাপারটা তাঁদের মনঃপূত নয়। বাবাকে তাঁরা কেউ কেউ বলেছেনও এ নিয়ে। কিন্তু বাবা বলেন–ওরা আসে, এজন্যে এক পয়সা নেয় না– অথচ সীতাকে ছবি আঁকা, সেলাইয়ের কাজ শেখাচ্ছে–কি ক’রে ওদের বলি তোমরা আর এসো না? তা ছাড়া ওরা এলে মেয়েদের সময়ও ভালোই কাটে, ওদের কেউ সঙ্গী নেই, এই নির্জন চা-বাগানের এক পাশে পড়ে থাকে–একটা লোকের মুখ দেখতে পায় না, কথা বলবার মানুষ পায় না–ওরা যদি আসেই তাতে লাভ ছাড়া ক্ষতি কি?
মায়ের মনের একটা গোপন ইচ্ছা ছিল, সেটা কিন্তু পূর্ণ হয়নি। বাবা অত্যন্ত মদ খান–এবং যেদিন খুব বেশী করে খেয়ে আসেন, সেদিন আমাদের বাংলো ছেড়ে পালাতে হয়। নইলে সবাইকে অত্যন্ত মারধোর করেন। সে সময়ে তাঁকে আমরা যমের মত ভয় করি–এক সীতা ছাড়া। সীতা আমাদের মত পালায় না–চা-ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে থাকতে চায় না। সে বাংলোতে থাকে, বলে–মারবে বাবা?..না হয় মরে যাবো–তা কি হবে? রোজ এ রকম ছুটোছুটি করার চেয়ে মরে যাওয়া ভালো। বাবার এই ব্যাপারের জন্যে আমাদের সংসারে শান্তি নেই–অথচ বাবা যখন প্রকৃতিস্থ থাকেন, তখন তাঁর মত মানুষ খুঁজে পাওয়া ভার–এত শান্ত মেজাজ। যখন যা চাই এনে দেন, কাছে ডেকে আদর করেন, নিয়ে খেলা করেন, বেড়াতে যান–কিন্তু মদ খেলেই একেবারে বদলে গিয়ে অন্য মূর্তি ধরেন, তখন বাংলো থেকে পালিয়ে যাওয়া ছাড়া আর আমাদের অন্য উপায় থাকে না।
মা’র ইচ্ছে ছিল মেমেদের ধর্মের এই বই পড়ে যদি বাবার মতিগতি ফেরে। মেমেরা মদ্যপানের কুফলের বর্ণনাসূচক ছোট ছোট বই দিয়ে যেতো–মা সেগুলো বাবার বিছানায় রেখে দিতেন–কে জানে বাবা পড়তেন কিনা–কিন্তু এই দেড় বৎসরের মধ্যে আমাদের মাসের মধ্যে তিন-চারবার চা-ঝোপের আড়ালে লুকনো বন্ধ হয়নি।
প্রায়ই আমি আর সীতা কোর্ট রোড ধরে বেড়াতে বেরুই। আমাদের বাগান থেকে মাইল দুই দূরে একটা ছোট ঘর আছে, আগে এখানে পোস্ট আপিস ছিল, এখন উঠে যাওয়াতে শুধু ঘরটা পড়ে আছে-উমপ্লাঙের ডাক-রানার ঝড়-বৃষ্টি বা বরফপাতের সময়ে এখানে মাঝে মাঝে আশ্রয় নেয়। এই ঘরটা আমাদের ভ্রমণপথের শেষসীমা, এর ওদিকে আমরা যাই না যে তা নয়, কিন্তু সে কালেভদ্রে, কারণ ওখান থেকে উমপ্লাং পর্যন্ত খাড়া উৎরাই নাকি এক মাইলের মধ্যে প্রায় এগারো শ ফুট নেমে গিয়েছে, মিস নর্টনের মুখে শুনেচি–যদিও বুঝি নে তার মানে কি। আমাদের অত দূরে যাওয়ার প্রয়োজনও ছিল না, যা আমরা চাই তা পোস্ট আপিসের ভাঙা ঘর পর্যন্ত গেলেই যথেষ্ট পেতাম–দু-ধারে ঘন নির্জন বন। আমাদের বাগানের নীচে গেলে আর সরল গাছ নেই–বনের তলা আর পরিষ্কার নেই, পাইন বন নেই, সে বন অনেক গভীর, অনেক নিবিড়, যেমন দুষ্প্রবেশ্য তেমনি অন্ধকার, কিন্তু আমাদের এত ভাল লাগে! বনে ফুলের অন্ত নেই–শীতে ফোটে বুনো গোলাপ, গ্রীষ্মকালে রডোডেনড্রন বনের মাথায় পাহাড়ের দেওয়ালে লাল আগুনের বন্যা আনে, গায়ক পাখীরা মার্চ মাসের মাঝামাঝি থেকে চারিধারের নির্জন বনানী গানে মুখরিত করে তোলে। ঝর্ণা শুকিয়ে গেলে আমরা শুকনো ঝর্ণার পাশের পথে পাথর ধরে ধরে নীচের নদীতে নামতাম–অতি সন্তর্পণে পাহাড়ের দেওয়াল ধ’রে ধ’রে, সীতা পেছনে, আমি আগে। দাদাও এক-একদিন আসতো, তবে সাধারণত সে আমাদের এই সব ব্যাপারে যোগ দিতে ভালবাসে না।
এক-একদিন আমি একাই আসি। নদীর খাতটা অনেক নীচে–তার পথ পাহাড়ের গা বেয়ে বেয়ে নীচে নেমে গিয়েচে–যেমন পিছল তেমনি দুর্গম–নদীর খাতে একবার পা দিলে মনে হয় যেন একটা অন্ধকার পিপের মধ্যে ঢুকে গিয়েচি। দু-ধারে খাড়া পাহাড়ের দেওয়াল উঠেচে–জল তাদের গা বেয়ে ঝরে পড়চে জায়গায় জায়গায়–কোথাও অনাবৃত, কোথাও গাছপালা, বনফুল, লতা–মাথার ওপরে আকাশটা যেন নীল কার্ট রোড–ঠিক অতটুকু চওড়া, ঐ রকম লম্বা, এদিকে-ওদিকে চলে গিয়েছে, মাঝে মাঝে টুকরো মেঘ কার্ট রোড বেয়ে চলেচে, কখনও বা পাহাড়ের এ-দেওয়াল ও-দেওয়াল পার হয়ে চলে যাচ্ছে–মেঘের ঐ খেলা দেখতে আমার বড় ভাল লাগত। নদী-খাতের ধারে একখানা শেওলা ঢাকা ঠাণ্ডা পাথরের ওপর বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মুখ উঁচু করে চেয়ে চেয়ে দেখতাম–বাড়ি ফিরবার কথা মনেই থাকত না।
মাঝে মাঝে আমার কি একটা ব্যাপার হ’ত। ওই রকম নির্জন জায়গায় কতবার একটা জিনিস দেখেচি।..
হয়তো দুপুরে চা-বাগানের কুলীরা কাজ সেরে সরল গাছের তলায় খেতে বসেচে– বাবা ম্যানেজারের বাংলোতে গিয়েচেন, সীতা ও দাদা ঘুমুচ্ছে–আমি কাউকে না জানিয়ে চুপি চুপি বেরিয়ে কার্ট রোড ধরে অনেক দূরে চলে যেতাম–আমাদের বাসা থেকে অনেক দূরে উমপ্লাঙের সেই পোড়ো পোস্ট আপিস ছাড়িয়েও চলে যেতাম–পথ ক্রমে যত নীচে নেমেছে, বনজঙ্গল ততই ঘন, ততই অন্ধকার, লতাপাতায় জড়াজড়ি ততই বেশী–বেতের বন, বাঁশের বন শুরু হ’ত–ডালে ডালে পরগাছা ও অর্কিড ততই ঘন, পাখী ডাকত–সেই ধরনের একটা নিস্তব্ধ স্থানে একা গিয়ে বসতাম।
চুপ করে বসে থাকতে থাকতে দেখেছি অনেক দূরে পাহাড়ের ও বনানীর মাথার ওপরে নীলাকাশ বেয়ে যেন আর একটা পথ–আর একটা পাহাড়শ্রেণী–সব যেন মৃদু হলুদ রঙের আলো দিয়ে তৈরি–সে অন্য দেশ, সেখানেও এমনি গাছপালা, এমনি ফুল ফুটে আছে, হলুদ আলোর বিশাল জ্যোতির্ময় পথটা এই পৃথিবীর পর্বতশ্রেণীর ওপর দিয়ে শূন্য ভেদ করে মেঘরাজ্যের ওদিকে কোথায় চলে গিয়েছে–দূরে আর একটা অজানা লোকালয়ে বাড়িঘর, তাদের লোকজনও দেখেচি, তারা আমাদের মত মানুষ না–তাদের মুখ ভাল দেখতে পেতাম না–কিন্তু তারাও আমাদের মত ব্যস্ত, হলুদ রঙের পথটা তাদের যাতায়াতের পথ। ভাল করে চেয়ে চেয়ে দেখেছি সে-সব মেঘ নয়, মেঘের ওপর পাহাড়ী রঙের খেলার ধাঁধা নয়–সে-সব সত্যি, আমাদের এই পৃথিবীর মতই তাদের বাড়িঘর, তাদের অধিবাসী, তাদের বনপর্বত, সত্যি-আমার চোখের ভুল যে নয় এ আমি মনে মনে বুঝতাম, কিন্তু কাউকে বলতে সাহস হ’ত না–মাকে না, এমন কি সীতাকেও না–পাছে তারা হেসে উঠে সব উড়িয়ে দেয়।
এ রকম একবার নয়, কতবার দেখেছি। আগে আগে আমার মনে হত আমি যেমন দেখি, সবাই বোধ হয় ওরকম দেখে। কিন্তু সেবার আমার ভুল ভেঙে যায়। আমি একদিন মাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম–আচ্ছা মা, পাহাড়ের ওদিকে আকাশের গায়ে ও-সব। কি দেখা যায়?…
মা বললেন–কোথায় রে?
—ওই কার্ট রোডের ধারে বেড়াতে গিয়ে এক জায়গায় বসেছিলাম, তাই দেখলাম আকাশের গায়ে একটা নদী–আমাদের মত ছোট নদী নয়–সে খুব বড়, কত গাছপালা–দেখনি মা?
–দূর পাগলা–ও মেঘ, বিকেলে ওরকম দেখায়।
–না মা, মেঘ নয়, মেঘ আমি চিনিনে? ও আর একটা দেশের মত, তাদের লোকজন পষ্ট দেখেচি যে–তুমি দেখনি কখনও?
–আমার ওসব দেখবার সময় নেই, ঘরের কাজ তাই ঠেলে উঠতে পারিনে, নিতুটার আবার আজ প’ড়ে পা ভেঙে গিয়েচে–আমার মরবার অবসর নেই–ও-সব তুমি দেখগে বাবা।
বুঝলাম মা আমার কথা অবিশ্বাস করলেন। সীতাকেও একবার বলেছিলাম–সে কথাটা বুঝতেই পারলে না। দাদাকে কখনো কিছু বলিনি।
আমার মনে অনেকদিন ধরে এটা একটা গোপন রহস্যের মত ছিল–যেন আমার একটা কি কঠিন রোগ হয়েছে–সেটা যাদের কাছে বলছি, কেউ বুঝতে পারছে না, ধরতে পারছে না, সবাই হেসে উড়িয়ে দিচ্ছে। এখন আমার সয়ে গিয়েছে। বুঝতে পেরেছি–ও সবাই দেখে না–যারা দেখে, চুপ করে থাকাই তাদের পক্ষে সব চেয়ে ভালো।
আমাদের বাসা থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা সব সময়ই চোখে পড়ে। জ্ঞান হয়ে পর্যন্ত দেখে আসছি বহুদূর দিকচক্রবালের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত তুষারমৌলি গিরিচূড়ার সারি–বাগানের চারিধারের পাহাড়শ্রেণীর যেন একটুখানি ওপরে বলে মনে হত-তখনো পর্যন্ত বুঝিনি যে ওগুলো কত উঁচু। কাঞ্চনজঙ্ঘা নামটা অনেকদিন পর্যন্ত জানতাম না, আমাদের চাকর থাপাকে জিজ্ঞেস করলে বলত, ও সিকিমের পাহাড়, সেবার বাবা আমাদের সবাইকে সীতা বাদে দার্জিলিং নিয়ে গিয়েছিলেন বেড়াতে–বাবার পরিচিত এক হিন্দুস্থানী চায়ের এজেন্ট ওখানে থাকে, তার বাসায় গিয়ে দু-দিন আমরা মহা আদর-যত্নে কাটিয়েছিলাম–তখন বাবার মুখে প্রথম শুনবার সুযোগ হল যে ওর নাম কাঞ্চনজঙ্ঘা। সীতার সেবার যাওয়া হয়নি, ওকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে বাবা বাজার থেকে ওর জন্যে রঙীন গার্টার, উল আর উল বুনবার কাঁটা কিনে এনেছিলেন।
এই কাঞ্চনজঙ্ঘার সম্পর্কে আমার একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা আছে …।
সেদিনটা আমাদের বাগানের কলকাতা আপিসের বড় সাহেব আসবেন বাগান দেখতে। তাঁর নাম লিন্টন সাহেব। বাবা ও ছোট সাহেব তাকে আনতে গিয়েছেন সোনাদা স্টেশনে–আমাদের বাগান থেকে প্রায় তিন-চার ঘণ্টার পথ। ঘোড়া ও কুলী সঙ্গে গিয়েছে। তখন মেমেরা পড়াতে আসত না, বিকেলে আমরা ভাইবোনে মিলে বাংলোর উঠোনে লাট্টু খেলছিলাম। সূর্য অস্ত যাবার বেশী দেরি নেই- মা রান্নাঘরে কাপড় কাচবার জন্যে সোডা সাবান জল ফোটাচ্ছিলেন, থাপা লণ্ঠন পরিষ্কারের কাজে খুব ব্যস্ত–এমন সময় আমার হঠাৎ চোখ পড়ল কাঞ্চনজঙ্ঘার দূর শিখররাজির ওপর আর একটা বড় পর্বত, স্পষ্ট দেখতে পেলাম তাদের ঢালুতে ছোট-বড় ঘরবাড়ি, সমস্ত ঢালুটা বনে ঢাকা, দেবমন্দিরের মত সরু সরু ঘরবাড়ির চূড়া ও গম্বুজগুলো অদ্ভুত রঙের আলোয় রঙীন– অস্তসূর্যের মায়াময় আলো যা কাঞ্চনজঙ্ঘার গায়ে পড়েছে তা নয়–তা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ও সম্পূর্ণ অপূর্ব ধরনের। সে-দেশ ও ঘরবাড়ি যেন একটা বিস্তীর্ণ মহাসাগরের তীরে–কাঞ্চনজঙ্ঘার মাথার ওপর থেকে সে মহাসাগর কতদূর চলে গিয়েছে, আমাদের এদিকেও এসেছে, ভুটানের দিকে গিয়েছে। তার কূলকিনারা নেই যদি কাউকে দেখাতাম সে হয়তো বলত আকাশ ওইরকম দেখায়, আমায় বোকা বলত। কিন্তু আমি বেশ জানি যা দেখচি তা মেঘ নয়, আকাশ নয়–সে সত্যিই সমুদ্র। আমি সমুদ্র কখনো দেখিনি, তাই কি, সমুদ্র কি রকম তা আমি জানি। বাবার মুখে গল্প শুনে আমি যে রকম ধারণা করেছিলাম সমুদ্রের, কাঞ্চনজঙ্ঘার উপরকার সমুদ্রটা ঠিক সেই ধরনের। এর বছর দুই পরে মেমেরা আমাদের বাড়ি পড়াতে আসে, তারা দাদাকে একখানা ছবিওয়ালা ইংরেজী গল্পের বই দিয়েছিল, বইখানার নাম রবিনসন ক্রুশো–তাতে নীল সাগরের রঙীন ছবি দেখেই হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল, এ আমি দেখেছি, জানি–আরও ছেলেবেলায় কাঞ্চনজঙ্ঘার মাথার ওপর এক সন্ধ্যায় এই ধরনের সমুদ্র আমি দেখেছিলাম–কূলকিনারা নেই, অপার…ভুটানের দিকে চলে গিয়েছে…
মিস নর্টনকে এ-সব কথা বলবার আমার ইচ্ছে ছিল। অনেকদিন মিস নর্টন আমায় কাছে ডেকে আদর করেছে, আমার কানের পাশের চুল তুলে গিয়ে আমার মুখ দু-হাতের তেলোর মধ্যে নিয়ে কত কি মিষ্টি কথা বলেছে, হয়তো অনেক সময়–তখন বুড়ী মেম ছাড়া ঘরের মধ্যে কেউ ছিল না–অনেকবার ভেবেছি এইবার বলব–কিন্তু বলি-বলি করেও আমার সে গোপন কথা মিস নর্টনকে বলা হয়নি। কথা বলা তো দূরের কথা, আমি সে-সময়ে মিস নর্টনের মুখের দিকে লজ্জায় চাইতে পারতাম না–আমার মুখ লাল হয়ে উঠত, কপাল ঘেমে উঠত…সারা শরীরের সঙ্গে জিবও যেন অবশ হয়ে থাকত…চেষ্টা করেও আমি মুখ দিয়ে কথা বার করতে পারতাম না। অথচ আমার মনে হত এবং এখনো মনে হয় যদি কেউ আমার কথা বোঝে, তবে মিস নর্টনই বুঝবে।
মাস দুই আগে আমাদের বাড়িতে এক নেপালী সন্ন্যাসী এসেছিলেন। পচাং বাগানের বড়বাবু বাবার বন্ধু, তিনি বাবার ঠিকানা দেওয়াতে সন্ন্যাসীটি সোনাদা স্টেশনে যাবার পথে আমাদের বাসায় আসেন। তিনি একবেলা আমাদের এখানে ছিলেন, যাবার সময় বাবা টাকা দিতে গিয়েছিলেন, তিনি নেননি। সন্ন্যাসী আমায় দেখেই কেমন একটু বিস্মিত হলেন, কাছে ডেকে তাঁর পাশে বসালেন, আমার মুখের পানে বার বার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাইতে লাগলেন–আমি কেমন একটু অস্বস্তি বোধ করলাম, তখন সেখানে আর কেউ ছিল না। তারপর তিনি আমার হাত দেখলেন, কপাল দেখলেন, ঘাড়ে কি দাগ দেখলেন। দেখা শেষ করে তিনি চুপ করে রইলেন, কিন্তু চলে যাবার সময় বাবাকে নেপালী ভাষায় বললে–তোমার এই ছেলে সুলক্ষণযুক্ত, এ জন্মেছে কোথায়?
বাবা বললেন–এই চা-বাগানেই।
সন্ন্যাসী আর কিছু না বলেই চলে যাচ্ছিলেন, বাবা এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন– ওর হাত কেমন দেখলেন?
সন্ন্যাসী কিছু জবাব দিলেন না, ফিরলেনও না, চলে গেলেন।
আমি কিন্তু বুঝতে পেরেছিলাম। আমি মাঝে মাঝে নির্জনে যে অন্যান্য অদ্ভুত জিনিস দেখি সন্ন্যাসী সে সম্বন্ধেই বলেছিলেন। সে যে আর কেউই বুঝবে না, আমি তা জানতাম। সেই জন্যেই তো আজকাল কাউকে ও-সব কথা বলিওনে।
পচাং চা-বাগানের কেরানীবাবু ছিলেন বাঙালী। তাঁর স্ত্রীকে আমরা মাসীমা বলে ডাকতাম। তিনি তাঁর বাপের বাড়ি গিয়েছিলেন রংপুরে, সোনাদা স্টেশন থেকে ফিরবার পথে মাসীমা আমাদের বাসায় মায়ের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। মা না খাইয়ে তাঁদের ছাড়লেন না, খেতে দেতে বেলা দুপুর গড়িয়ে গেল। আমাদের বাসা থেকে পচাং বাগান তিন মাইল দূরে, ঘন জঙ্গলের মধ্যবর্তী সরু পথ বেয়ে যেতে হয়, মাঝে মাঝে চড়াই উৎরাই। আমি সীতা ও দাদা তাঁদের সঙ্গে এগিয়ে দিতে গেলাম–পচাং পৌঁছতে বেলা তিনটে বাজল। আমরা তখনই চলে আসছিলাম, কিন্তু মাসীমা ছাড়লেন না, তিনি ময়দা মেখে পরোটা ভেজে, চা তৈরি করে আমাদের খাওয়ালেন রাত্রে থাকবার জন্যও অনেক অনুরোধ করলেন, কিন্তু আমাদের ভয় হ’ল বাবাকে না বলে আসা হয়েছে–বাড়ি না ফিরলে বাবা আমাদেরও বকবেন, মাও বকুনি খাবেন। বনজঙ্গলের পথ হ’লেও আরো অনেকবার আমরা মাসীমার এখানে এসেচি। আমি একাই কতবার এসেচি গিয়েচি। আমরা যখন রওনা হই তখন বেলা খুব কম আছে। অন্ধকার এরই মধ্যে নেমে আসছে–আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, ঝড়বৃষ্টির খুব সম্ভাবনা। পচাং বাগান থেকে আধ মাইল যেতেই ঘন জঙ্গল–বড় বড় ওক আর পাইন-আবার উৎরাইয়ের পথে নামলেই জঙ্গল অন্য ধরনের, আরো নিবিড় গাছের ডালে পুরু কম্বলের মত শেওলা ঝুলছে, ঠিক যেন অন্ধকারে অসংখ্য ভূত-প্রেত ডালে নিঃশব্দে দোল খাচ্ছে। সীতা খুশির সুরে বললে– দাদা, যদি আমাদের সামনে ভালুক পড়ে?…হি হি–
সীতার ওপর আমাদের ভারি রাগ হ’ল, সবাই জানে এ পথে ভালুকের ভয় কিন্তু সে কথা ওর মনে করিয়ে দেওয়ার দরকার কি ছিল? বাহাদুরি দেখাবার বুঝি সময় অসময় নেই?
অন্ধকার ক্রমেই খুব ঘন হয়ে এল, আর খানিকটা গিয়ে সরু পায়ে-চলার পথটা বনের মধ্যে কোথাও হারিয়ে গেল–সঙ্গে সঙ্গে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি শুরু হল–তেমনি কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া। শীতে হাত-পা জমে যাওয়ার উপক্রম হ’ল। গাছের ডালে শেওলা বৃষ্টিতে ভিজে এত ধরনের গন্ধ বার হয় এ আমরা সকলেই জানতাম, কিন্তু সীতা বার বার জোর করে বলতে লাগল ও ভালুকের গায়ের গন্ধ।–দাদা আমাদের আগে আগে যাচ্ছিল, মাঝখানে সীতা, পেছনে আমি–হঠাৎ দাদা থমকে দাঁড়িয়ে গেল। সামনে একটা ঝর্ণা–তার ওপরটায় কাঠের গুঁড়ির পুল ছিল–পুলটা ভেঙে গিয়েছে। সেটার তোড় যেমন বেশী, চওড়াও তেমনি। পার হ’তে সাহস করা যায় না। দাদা বললে–কি হবে জিতু…চল পচাঙে মাসিমার কাছে ফিরে যাই। সীতা বললে–বাবা পিঠের ছাল তুলবে আজ না ফিরে গেলে বাসায়। না দাদা, বাড়িই চলো।
দাদা ভেবে বললে–এক কাজ করতে পারবি? পাকদণ্ডীর পথে ওপরে উঠতে যদি পারিস–ওখান দিয়ে লিন্টন বাগানের রাস্তা। আমি চিনি, ওপরে জঙ্গলও কম। যাবি?
দাদা তা হলে খুব ভীতু তো নয়!
পাকদণ্ডীর সে পথটা তেমনি দুর্গম, সারা পথ শুধু বন জঙ্গল ঠেলে ঠেলে উঠতে হবে, পা একটু পিছলে গেলেই, কি বড় পাথরের চাঁই আলগা হয়ে খসে পড়লে আটশ’ কি হাজার ফুট নীচে পড়ে চুরমার হতে হবে। অবশেষে ঘন বনের বৃষ্টিভেজা পাতা-লতা, পাথরের পাশের ছোট ফার্নের ঝোপ ঠেলে আমরা ওপরে ওঠাই শুরু করলাম–অন্য কোনো উপায় ছিল না। কাপড়-চোপড় মাথার চুল বৃষ্টিতে ভিজে একাকার হয়ে গেল– রক্ত জমে হাত-পা নীল হয়ে উঠল। পাকদণ্ডীর পথ খুব সরু, দুজন মানুষে কোনোগতিকে পাশাপাশি যেতে পারে, বাঁয়ে হাজার ফুট খাদ, ডাইনে ঈষৎ ঢালু পাহাড়ের দেওয়াল খাড়া উঠেছে তাও হাজার-বারোশ ফুটের কম নয়। বৃষ্টিতে পথ পিছল, কাজেই আমরা ডাইনের দেওয়াল ঘেঁষে-ঘেঁষেই উঠছি। পথ মানুষের কেটে তৈরি করা নয় বলেই হোক, কিংবা এ-পথে যাতায়াত নেই বলেই হোক–ছোটখাটো গাছপালার জঙ্গল খুব বেশী। ডাইনের পাহাড়ের গায়ে বড় গাছের ডালপালাতে সারা পথটা ঝুপসি ক’রে রেখেছে, মাঝে মাঝে সেগুলো এত নিবিড় যে সামনে কি আছে দেখা যায় না।
হঠাৎ একটা শব্দ শুনে আমরা ক’জনই থমকে দাঁড়ালুম। সবাই চুপ করে গেলাম। আমরা বুঝতে পেরেছিলাম শব্দটা কিসের। ভয়ে আমাদের বুকের স্পন্দন বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হ’ল। সীতাকে আমি জড়িয়ে ধরে কাছে নিয়ে এলুম। অন্ধকারে আমরা কিছু দেখতে পাচ্ছিলাম না বটে, কিন্তু আমরা জানতাম ভালুক যে পথে আসে পথের ছোটখাটো গাছপালা ভাঙতে ভাঙতে আসে। একটা কোনো ভারী জানোয়ারের অস্পষ্ট পায়ের শব্দের সঙ্গে কাঠকুটো ভাঙার শব্দে আমাদের সন্দেহ রইল না যে, আমরা যে-পথ দিয়ে এইমাত্র উঠে এসেছি, সেই পথেই ভালুক উঠে আসছে আমাদের পেছন পেছন। আমরা প্রাণপণে পাহাড় ঘেঁষে দাঁড়ালাম, ভরসা যদি অন্ধকারে না দেখতে পেয়ে সামনের পথ দিয়ে চলে যায়…আমরা কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে আছি, নিঃশ্বাস পড়ে কি না-পড়ে–এমন সময়ে পাকদণ্ডীর মোড়ে একটা প্রকাণ্ড কালো জমাট অন্ধকারের স্তূপ দেখা গেল–স্তূপটা একবার ডাইনে একবার বাঁয়ে বেঁকে বেঁকে আসছে–যতটা ডাইনে, ততটা বাঁয়ে নয়–আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেখান থেকে দশ গজের মধ্যে এল–তার ঘন ঘন হাঁপানোর ধরনের নিঃশ্বাসও শুনতে পাওয়া গেল–আমাদের নিজেদের নিঃশ্বাস তখন আর বইছে না..কিন্তু মিনিটখানেকের জন্য–একটু পরেই আর স্তূপটাকে দেখতে পেলাম না–যদিও শব্দ শুনে বুঝলাম সেটা পাকদণ্ডীর ওপরকার পাহাড়ী ঢালুর পথে উঠে যাচ্ছে। আরো দশ মিনিট আমরা নড়লাম না, তারপর বাকী পথটা উঠে এসে লিন্টন বাগানের রাস্তা পাওয়া গেল। আধ মাইল চলে আসবার পরে উমপ্লাঙের বাজার। এই বাজারের অমৃত সাউ মিঠাই দেয় আমাদের বাসায় আমরা জানতাম–দাদা তার দোকানটাও চিনত। দোরে ধাক্কা দিয়ে ওঠাতে সে বাইরে এসে আমাদের দেখে অবাক হয়ে গেল। আমাদের তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে আগুনের চারিধারে বসিয়ে দিলে–আগুনে বেশী কাঠ দিলে ও বড় একটা পেতলের লোটায় চায়ের জল চড়ালে। তার বৌ উঠে আমাদের শুকনো কাপড় দিলে পরবার ও ময়দা মাখতে বসল। রাত তখন দশটার কম নয়। আমরা বাসায় ফিরবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে পড়েছি–বললাম–আমরা কিছু খাব না, আমরা এবার যাই। অমৃত সাউ একা আমাদের ছেড়ে দিলে না, তার ভাইকে সঙ্গে পাঠালে। রাত প্রায় সাড়ে এগারোটার সময় বাগানে ফিরে এসে দেখি হৈ হৈ কাণ্ড। বাবা বাসায় নেই, তিনি সেদিন খুব মদ খেয়েছিলেন, ফেরেননি, তার ওপরে আমরাও ফিরিনি, মা পচাঙে লোক পাঠিয়েছিলেন, সে লোক ফিরে এসে বলেছে ছেলেমেয়েরা তো সন্ধ্যের আগেই সেখান থেকে রওনা হয়েছে। এদিকে নাকি খুব ঝড় হয়ে গিয়েছে, আমরা আরও উঁচুতে থাকবার জন্যে ঝড় পাইনি–নীচে নাকি অনেক গাছপালা ভেঙে পড়েছে। এই সব ব্যাপারে মা ব্যস্ত হয়ে সাহেবের বাংলোয় খবর পাঠান–ছোট সাহেব চারিধারে আমাদের খুঁজতে লোক পাঠিয়েছে। মা এতক্ষণ কাঁদেননি, আমাদের দেখেই জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠলেন–সে এক ব্যাপার আর কি!
কিন্তু পরদিন যে ঘটনা ঘটল তা আরও গুরুতর। পরদিন চা-বাগানে বাবার চাকরি গেল। কেন গেল তা জানি না। অনেক দিন থেকেই সাহেবরা নাকি বাবার ওপর সন্তুষ্ট ছিল না, সেল মাস্টার বাগান দেখতে এসে বাবার নামে কোম্পানির কাছে কয়েকবার রিপোর্টও করেছিল, বাবা মদ খেয়ে ইদানীং কাজকর্ম নাকি ভাল করে করতে পারতেন না, এই সব জন্যে। আমরা যে-রাত্রে পথ হারিয়ে যাই, সে-রাত্রে বাবা মদ খেয়ে বেহুঁশ হয়ে কুলী লাইনের কোথায় পড়েছিলেন–বড় সাহেব সেজন্যে ভারি বিরক্ত হয়। আরো কি ব্যাপার হয়েছিল না হয়েছিল আমরা সে-সব কিছু শুনিনি।
বাবা যখন সহজ অবস্থায় থাকতেন, তখন তিনি দেবতুল্য মানুষ। তখন তিনি আমাদের ওপর অত্যন্ত স্নেহশীল, অত ভালোবাসতে মাও বোধ হয় পারতেন না। আমরা যা চাইতাম বাবা দার্জিলিং কি শিলিগুড়ি থেকে আনিয়ে দিতেন। আমাদের চোখছাড়া করতে চাইতেন না। আমাদের নাওয়ানো-খাওয়ানোয় গোলমাল বা এতটুকু ব্যতিক্রম হলে মাকে বকুনি খেতে হ’ত। কিন্তু মদ খেলেই একেবারে বদলে যেতেন, সামান্য ছল ছুতোয় আমাদের মারধর করতেন। হয়তো আমায় বললেন এক্সারসাইজ করিস নে কেন? বলেই ঠাস করে এক চড়। তারপর বললেন–উঠবস কর। আমি ভয়ে ভয়ে একবার উঠি আবার বসি–হয়তো ত্রিশ-চল্লিশবার করে করে পায়ে খিল ধ’রে গেল– বাবার সেদিকে খেয়াল নেই। মা থাকতে না পেরে এসে আমাদের সামলাতেন। সেইজন্যে ইদানীং বাবা সহজ অবস্থায় না থাকলেই আমরা বাসা থেকে পালিয়ে যাই–কে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খাবে?
এই সবের দরুন আমরাও বাবাকে ভয় যতটা করি ততটা ভালোবাসিনে।
দু-চারদিন ধরে বাবা-মায়ে পরামর্শ চলল, কি করা যাবে এ অবস্থায়। আমরা বাইরে বাইরে বেড়াই কিন্তু সীতা সব খবর রাখে। একদিন সীতাই চুপিচুপি আমায় বললে– শোনো দাদা, আমরা আমাদের দেশে ফিরে যাব বাবা বলেছে। বাবার হাতে এখন টাকাকড়ি নেই কিনা–তাই দেশে ফিরে দেশের বাড়িতে থেকে চাকরির চেষ্টা করবে। শীগগির যাব আমরা–বেশ মজা হবে দাদা–না? …দেশে চিঠি লেখা হয়েছে–
আমরা কেউ বাংলা দেশ দেখিনি, আমাদের জন্ম এখানেই। দাদা খুব ছেলেবেলায় একবার দেশে গিয়েছিল মা-বাবার সঙ্গে, তখন ওর বয়স বছর তিনেক–সে-কথা ওর মনে নেই। আমরা তো আজন্ম এই পর্বত, বনজঙ্গল, শীত, কুয়াশা, বরফ-পড়া দেখে আসছি–কল্পনাই করতে পারিনে এ-সব ছাড়া আবার দেশ থাকা সম্ভব। তা ছাড়া সমাজের মধ্যে কোনো দিন মানুষ হইনি বলে আমরা কোনো বন্ধনে অভ্যস্ত ছিলাম না, সামাজিক নিয়ম-কানুনও ছিল আমাদের সম্পূর্ণ অজানা। মানুষ হয়েছি এরই মধ্যে, যেখানে খুশী গিয়েছি, যা খুশী করেছি। কাজেই বাংলা দেশে ফিরে যাওয়ার কথা যখন উঠল, তখন একদিকে যেমন অজানা জায়গা দেখবার কৌতূহলে বুক ঢিপ ঢিপ করে উঠল, অন্যদিকে মনটা যেন একটু দমে গেল।
থাপাকে বিদায় দেওয়া হ’ল। সে আমাদের মানুষ করেছিল, বিশেষ করে সীতাকে। তাকে এক মাসের বেশী মাইনে, দুখানা কাপড় আর বাবার একটা পুরোনো কোট দেওয়া হ’ল। থাপা বেশ সহজ ভাবেই বিদায় নিলে, কিন্তু বিকালে আবার ফিরে এসে বললে সে আমাদের যাওয়ার দিন শিলিগুড়ি পর্যন্ত নামিয়ে দিয়ে তবে নিজের গাঁয়ে ফিরে যাবে। শিলিগুড়ি স্টেশনে সে আমাদের সবাইকে সন্দেশ কিনে খাওয়ালে–ওর মাইনের টাকা থেকেই বোধ হয়। মা রাঁধলেন, সে সব যোগাড় করে দিলে। ট্রেন যখন ছাড়ল তখনও থাপা প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে বোকার মত হাসছে।
কাঞ্চনজঙ্ঘাকে ভালবাসি, সে যে আমাদের ছেলেবেলা থেকে সাথী, এই বিরাট পর্বত প্রাচীর, ওক-পাইনের বন, অর্কিড, শেওলা, ঝর্ণা, পাহাড়ী নদী মেঘ-রোদ-কুয়াশার খেলা– এরই মধ্যে আমরা জন্মেছি–এদের সঙ্গে আমাদের বত্রিশ নাড়ীর যোগ …তখন এপ্রিল মাস, আবার পাহাড়ের ঢালুতে রাঙা রডোডেনড্রন ফুলের বন্যা এসেছে–সারা পথ দাদা বলতে বলতে এল চুপিচুপি–কেন বাবা অত মদ খেতেন, তা না হলে তো আর চাকরি যেত না–বাবারই তো দোষ!
.
০৩.
আমাদের দেশের গ্রামে পৌঁছলাম পরদিন বেলা নটার সময়ে। বাবার মুখে শুনেছিলাম গ্রামের নাম আটঘরা, স্টেশন থেকে মাইল দুই আড়াই দূরে, জেলা চব্বিশ-পরগণা। এত বাঙালী পরিবারের বাস একসঙ্গে দেখে মনে বড় আনন্দ হ’ল। আমরা কখনো ফসলের ক্ষেত দেখিনি, বাবা চিনিয়ে দিলেন পাটের ক্ষেত্র কোনটা, ধানের ক্ষেত কোনটা। এ ধরনের সমতলভূমি আমরা দেখিনি কখনো–রেলে আসবার সময় মনের অভ্যাসে কেবলই ভাবছিলাম এই বড় মাঠটা ছাড়ালেই বুঝি পাহাড় আরম্ভ হবে। সেটা পার হয়ে গেলে মনে হচ্ছিল এইবার নিশ্চয়ই পাহাড়। কিন্তু পাহাড় তো কোথাও নেই, জমি উঁচু-নীচুও নয়, কি অদ্ভুত সমতল! যতদূর এলাম শিলিগুড়ি থেকে সবটা সমতল-ডাইনে, বাঁয়ে, সামনে, সবদিকে সমতল, এ এক আশ্চর্য ব্যাপার। দাদা এর আগে সমতলভূমি দেখেছে, কারণ সে জন্মেছিল হনুমান নগরে, নতুন অভিজ্ঞতা হ’ল আমার ও সীতার।
আমাদের বাড়িটা বেশ বড়, দোতলা, কিছু পুরনো ধরনের। বাড়ির পেছনে বাগান, ছোট একটা পুকুর। আমরা যখন গাড়ি থেকে নামলাম–বাড়ির মেয়েরা কেউ কেউ দোরের কাছে দাঁড়িয়েছিলেন, তার মধ্যে জ্যাঠাইমা, কাকীমারাও ছিলেন। মা বললেন, প্রণাম করো। পাড়ার অনেক মেয়ে দেখতে এসেছিলেন, তাঁরা সীতাকে দেখে বলাবলি করতে লাগলেন, কি চমৎকার মেয়ে দেখেছ? এমন রঙ আমাদের দেশে হয় না, পাহাড়ের দেশে ব’লে হয়েছে। দাদাকে নিয়েও তারা খুব বলাবলি করলে, দাদার ও সীতার রঙ নাকি ‘দুধে-আলতা’–আমার মুখের চেয়ে দাদার মুখ সুন্দর, এ-সব কথা আমরা শুনলাম। চা-বাগানে এ-সব কথা কেউ বলেনি। আর একটা লক্ষ্য করলাম আমাদের গাঁয়ের মেয়েরা প্রায়ই কালো, চা-বাগানের অনেক কুলীমেয়ে এর চেয়ে ফর্সা।
আমাদের থাকার ঘর দেখে তো আমরা অবাক। এত বড় বাড়িতে এ-ঘরটা ছাড়া তো আরো কত ঘর রয়েছে! নীচের একটা ঘর, ঘরের ছাদে মাটির নীচের কড়িকাঠ ঝুলে পড়েছে বলে খুঁটির ঠেকনো। কেন ওপরে দোতলায় তো কত ঘর, এত বড় বাড়ি তো! অন্য ঘরে জায়গা হবে না কেন? এই খারাপ ঘরটাতে আমরা থাকবো কেন?
দেখলাম বাবা মা বিনা প্রতিবাদে সেই ঘরটাতেই আমাদের জিনিসপত্র তুললেন।
দিন-চারেক পরে জ্যাঠাইমা একদিন আমায় জিজ্ঞেস করলেন–হ্যাঁ রে, তোর মাকে নাকি সেখানে মেমে পড়াতো?
আমি বললাম, হ্যাঁ, জ্যাঠাইমা।
গর্বের সুরে বললাম–আমাকে, দাদাকে, সীতাকেও পড়াতো।
জ্যাঠাইমা বললেন–তাদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া ছিল নাকি তোদের?
আমি বাহাদুরি করে বললাম–তারা এসে চা খেত আমাদের বাড়ি। আমাদের বিস্কুট দিত, কেক দিত খেতে তাদের ওখানে গেলে–চা খাওয়াতো—
জ্যাঠাইমা টানা-টানা সুরে বললেন–মাগো মা! কি হবে, আমাদের ঘরে-দোরে তো যখন-তখন উঠছে, হিঁদুর ঘরে জাতজন্ম আর রইল না।
আমি তখন বুঝতে পারিনি কেন জ্যাঠাইমা এ রকম বলছেন। কিন্তু শুধু এ কথা নয়–আমি ছেলেমানুষ, অনেক কথাই তখন জানতাম না। জানতাম না যে এই বাড়িতে আমার বাবার অংশটুকু অনেক দিন বিক্রী হয়ে গিয়েছে, এখন যে এঁদো ঘরে আমরা আছি, সে ঘরে কোনো ন্যায্য অধিকার আমাদের নেই–জ্ঞাতি জ্যাঠামশাইরা অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞার সঙ্গে থাকতে দিয়েছেন মাত্র। জানতাম না যে, আমার বাবা বর্তমানে অর্থহীন, অসুস্থ ও চাকুরিহীন, সরিকের বাড়িতে আশ্রয়প্রার্থী। আরো জানতাম না যে, বাবা বিদেশে থাকেন, ইংরেজী জানেন ও ভাল চাকুরি করেন বলে এঁদের চিরদিন ছিল হিংসে–আজ এ অবস্থায় হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়ে তাঁরা যে এতদিনের সঞ্চিত গায়ের ঝাল মেটাতে ব্যগ্র হয়ে উঠবেন সেটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও ন্যায়সঙ্গত। চাকুরির অবস্থায় মাকে নিয়ে বাবা কয়েকবার এখানে এসে চাল দেখিয়েছিলেন, এঁরা সে-কথা ভোলেননি। ছেলেমানুষ বলেই এত কথা তখন বুঝতাম না।
আমরা কখনো দোতলা বাড়ি দেখিনি–গাঁয়ে ঘুরে ঘুরে দোতলা কোঠা বাড়ি দেখতে আমাদের ভারি ভালো লাগতো, বিশেষ করে সীতার। সীতা আজ এসে হয়তো বললে– কাল যেও আমার সঙ্গে দাদা, ও-পাড়ায় বাঁড়ুয্যে-বাড়ি কত বড় দেখে এসো–দোতলার ওপরে আবার একটা ছোট ঘর, সত্যি দাদা!
আমাদের গ্রামে খুব লোকের বাস–এক এক পাড়াতেই ষাট-সত্তর ঘর ব্রাহ্মণ। এত ঘন বসতি কখনো দেখিনি–কেমন নতুনতর মনে হয়, কিন্তু ভাল লাগে না। এতে যেন মন হাত পা ছড়াবার জায়গা পায় না। সদাই কেমন অস্বস্তি বোধ হয়–রাস্তায় বেজায় ধুলো, পুরনো নোনাধরা ইটের বাড়িই অধিকাংশ, বিশেষ কোনো শ্রীছাঁদ নেই–পথের ধারে মাঝে মাঝে গাছপালা, সে-সব গাছপালা আমি চিনি নে, নামও জানি নে, কেবল চিনি কচুগাছ ও লালবিছুটি। এদের হিমালয়ে দেখেছি বলে নয়, কচুর ডাঁটার তরকারি এখানে এসে খেয়েছি বলে। আর আমার খুড়তুতো ভাই বিশু একদিন সীতাকে বিছুটির পাতা দেখিয়ে বলেছিল–এর পাতা তুলে গায়ে ঘষতে পারিস?…বেচারী সীতা জানত না কিছু, সে বাহাদুরি দেখিয়ে একমুঠো পাতা তুলে বাঁ-হাতে আবছা করে ঘষেছিল–তারপর আর যায় কোথায়।
এ-সব জায়গা আমার চোখে অত্যন্ত কুশ্রী মনে হয়, মন ভরে ওঠে এমন একটা দৃশ্য এর কোনো দিকেই নেই–ঝর্ণা নেই, বরফে-মোড়া পর্বত-পাহাড় নেই–আরো কত কি নেই। সীতারও তাই, একদিন সে চুপিচুপি বললে–এখান থাকতে তোমার ইচ্ছে হয় দাদা? আমায় যদি এখুনি কেউ বলে চা-বাগানে চল, আমি বেঁচে যাই। আর একটা কথা শোনো দাদা–জ্যাঠাইমা কি খুড়ীমার ঘরে অত যেও না যেন। ওরা আমাদের দেখতে পারে না। ওদের বিছানায় গিয়ে বসেছিলে কেন দুপুরবেলা? তুমি উঠে গেলে কাকীমা তোমায় বললে, অসভ্য পাহাড়ী ভূত, আচার নেই বিচার নেই, যখন-তখন বিছানা ছোঁয়! যেও না ওদের ঘরে যখন-তখন, বুঝলে?
ছোট বোনের পরামর্শ বা উপদেশ নিতে আমার অগ্রজগর্ব সঙ্কুচিত হয়ে গেল, বললাম–যা যা, তোকে শেখাতে হবে না। কাকীমা মন্দ ভেবে কিছুই বলেননি, আমায় ডেকে তার পরে কত বুঝিয়ে দিলেন পাছে আমি রাগ করি। জানিস তা?
বলা বাহুল্য আমায় ডেকে কাকীমার কৈফিয়ত দেওয়ার কথাটা আমার কল্পনাপ্রসূত। আমাদের জীবনের যে অভিজ্ঞতা এই চার মাসের মধ্যেই সঞ্চয় করেছি, তা বোধ হয় সারা জীবনেও ভুলবো না। আমরা সত্যই জানতাম না যে, সংসারের মধ্যে এত সব খারাপ জিনিস আছে, মানুষ মানুষের প্রতি এত নিষ্ঠুর হতে পারে, যাদের কাছে জেঠিমা, কাকীমা, দিদি বলে হাসিমুখে ছুটে গিয়েছি, তারা এতটা হৃদয়হীন ব্যবহার সত্যিই করতে পারে! কি করে জানবই বা এ সব?
মুশকিল এই যে এত সাবধানে চললেও পদে পদে আমরা জ্যাঠাইমাদের কাকীমাদের কাছে অপরাধী হয়ে পড়ি। আমরা লোকালয়ে কখনো বসবাস করিনি বলেই হোক বা এদের এখানকার নিয়ম-কানুন জানিনে বলেই হোক, বুঝতে পারিনে যে কোথায় আমাদের অপরাধ ঘটছে বা ঘটতে পারে। রাত্রে যে কাপড়খানা পরে শুয়ে থাকি, সেইখানা পরনে থাকলে সকালে যে আলনা ছুঁতে নেই, তার দরুন আলনাসুদ্ধ কাচা কাপড় সব নোংরা হয়ে যায়, বা বাড়ির আশপাশের খানিকটা সুনির্দিষ্ট অংশ পবিত্র, কিন্তু সীমানা পেরিয়ে গেলেই হাত-পা না ধুয়ে বা গঙ্গাজল মাথায় না দিয়ে ঘরদোরে ঢুকতে নেই–এ-সব কথা আমরা জানিনে, শুনিওনি–যুক্তির দিক দিয়েও বুঝতে পারিনে। আমাদের বাড়ির খিড়কিতে খানিকটা বন, একদিন বিকেলে আমি, সীতা ও দাদা সেখানে কুঁড়েঘর বাঁধবার জন্যে নোনাগাছের ডাল কাটছি–কাকীমা দেখতে পেয়ে বললেন, ওখানে গিয়ে জুটেছ সব? ভাগ্যিস চোখে পড়ল! এক্ষুনি তো ওইসব নিয়ে উঠত এসে দোতলার দালানে!…মা গো মা, মেলেচ্ছ খিরিস্টানের মত ব্যাভার, আঁস্তাকুড়ে ঘেঁটে খেলা হচ্ছে দ্যাখো!
সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে চারিদিকে চেয়ে দেখলাম, আঁস্তাকুড়ের অন্য কোনো লক্ষণ তো নেই! দিব্যি পরিষ্কার জায়গা, ঘাসের জমি আর বনের গাছপালা। আমি অবাক হয়ে বললাম– কাকীমা, এখানে তো কিছু নোংরা নেই?…এসে দেখুন বরং কেমন পরিষ্কার–
কাকীমার মুখ দিয়ে খানিকক্ষণ কথা বার হ’ল না–তিনি এমন কথা জীবনে কখনো শোনেননি। তারপর বললেন–চোখে কি ঢ্যালা বেরিয়েছে নাকি? এঁটো হাঁড়িকলসী ফেলা রয়েছে দেখছ না সামনে?..কাচা কাপড় পরে কোন ছেলেমেয়েটা এই বিকেলে পথ থেকে অত দূরে বনজঙ্গলের মধ্যে যায়? ওটা আঁস্তাকুড় হ’ল না? আবার সমানে তককো!
তারপর খুড়ীমা হুকুম দিলেন আমাদের সবাইকে এক্ষুনি নাইতে হবে। আমরা অবাক হয়ে গেলাম–নাইতে হবে কেন?
সামনে হাত তিন-চারেক দূরে গোটাকতক ভাঙা হাঁড়িকুড়ি পড়ে আছে বটে, কিন্তু তার দরুন গোটা বনটা অপরিষ্কার কেন হবে তা বুঝতে পারলাম না আমরা তিনজনে কেউ বিশেষ করে এটা আরো বুঝতে পারলাম না যে, পথ থেকে দূরে বনের মধ্যে বিকেলে কাপড় প’রে যেতে দোষটা কিসের! চা-বাগানে থাকতে তো কত দূর দূর আমরা চলে যেতাম, কার্ট রোড, পচাঙের বাজার এখানেই বা কি বন, সেখানকার সেই সুনিবিড় বনানী পদচিহ্নহীন, নির্জন, আধ-অন্ধকার–কতদূরে, যেখানে যেখানে গিয়েছি কাপড় পরেই তো গিয়েছি–
দাদা একটু ভীতু, সে ভয়ে নাইতে রাজী হ’ল। আমি বললাম-সীতা, তুই আর আমি নাইবো না, কখখনো না।
আমি যা বলি তাই শোনা সীতার স্বভাব–সে বললে, খুড়ীমা খুন করে ফেললেও আমি নাইবো না দাদা।
খুড়ীমা আমাদের সাধ্যমত নির্যাতনের কোনো ত্রুটি করলেন না। বাড়ি ঢুকতে দিলেন না, তাঁর বড় ছেলে হারুদাকে বলে দিলেন আমাদের শাসন করতে, মাকে বললেন– তোমার ওই ডাকাত মেয়ে আর ডাকাত ছেলেকে আজ কি দশা করি তা টেরই পাবে– আমার সঙ্গে সমানে তককো তো করলেই আবার আমার কথার ওপর একগুয়েমি!
মা ওঁদের বাড়িতে এখন এসে রয়েছে, ভয়ে কিছু বলতে পারলেন না। আমি সীতাকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি থেকে চলে গেলাম। ও-পাড়ায় পথের ধারে শ্যাম বাগচীদের পোড়ো বাড়ি, পেছনে তাদের বাগান, সেও পোড়ো। সারাক্ষণ আমরা সেখানে কাটালাম, সন্ধ্যার সময় দাদা গিয়ে ডেকে আনলে। বাড়িতে ঢুকতে যাব কাকা দোতলা থেকে হেঁকে বললেন–ওদের বাড়ি ঢুকতে দিও না বলছি–ওরা যেন খবরদার আমার বাড়ি না মাড়ায়, সাবধান!–যেখানে হয় যাক, এত বড় আস্পদ্দা সব–
মা কিছু বলতে সাহস করলেন না, বৌমানুষ! বাবা বাড়ি ছিলেন না, চাকরির চেষ্টায় আজকাল তিনি বড় এখানে ওখানে ঘোরেন, কিছু পান না বোধ হয়–দু-একদিন পরে শুকনো মুখে ফিরে আসেন–সংসার একেবারে অচল। আমরা এক প্রহর রাত পর্যন্ত দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে রইলাম। জ্যাঠাইমা, খুড়ীমা, জ্যাঠামশাই, দিদিরা কেউ একটা কথাও বললেন না। তারপর যখন ওদের দোতলায় খাওয়া-দাওয়া সারা হ’ল, আলো নিবল, মা চুপিচুপি আমাদের বাড়িতে ঢুকিয়ে নিলেন, বললেন–জিতু, খুড়িমার কথা শুনলি নে কেন? ছি–
আমি বললাম–উনি যে কথা বলেন মা, তার কোনো মানে হয় না। আচ্ছা মা, তুমিই বলো আমরা সেখানে বনে বনে বেড়াতাম না? আমরা কি নাইতুম? আর বন কি আঁস্তাকুড়? অন্যায় কথা ওঁর কখখনো শুনব না মা। এতে উনি মারুন আর খুনই করুন–
মা অতি কষ্টে কান্না সামলাচ্চেন মনে হ’ল। বললেন–তুই যদি এরকম করিস তা হ’লে এ বাড়িতে ওরা আমাদের থাকতে দেবে না। আমাদের কি চেঁচিয়ে কথা বলবার জো আছে এখানে? ছি বাবা জিতু, ওরা যা বলে শুনবি। ওরা লোক ভাল না–আগে জানলে ভিক্ষে করে খেতাম, তবুও এখানে আসতাম না। তোর বাবার যে একটা কিছু হ’লে হয়।
বাবা কলকাতা থেকে দুপুরে বাড়ি ফিরলেন। কাপড়-জামা এত ময়লা কখনো বাবার গায়ে দেখিনি। আমায় কাছে ডেকে বললেন–শোন জিতু, এই পুঁটলিটা তোর মাকে দিয়ে আয়, আমি একবার ও-পাড়া থেকে আসি। ভটচায্যিদের নস্যির কারখানায় একটা লোকের নামে চিঠি দিয়েছে–ওদের দিয়ে আসি।
আমি বললাম–এখন যেও না বাবা। চিঠি আমি দিয়ে আসব’খন, তুমি বসে চা-টা খাও। বাবা শুনলেন না, চলে গেলেন। বাবার মুখ শুকনো, দেখে বুঝলাম যেজন্যে গিয়েছিলেন তার কোনো যোগাড় হয়নি, অর্থাৎ চাকরি। চাকরি না হলেও আর এদিকে চলে না।
হাতের টাকা ক্রমশ ফুরিয়ে এসেছে। আমরা নীচের যে ঘরে থাকি, গোরুবাছুরেরও সেখানে থাকতে কষ্ট হয়। আমরা এসেছি প্রায় মাস-চারেক হ’ল, এই চার মাসেই যা দেখেছি শুনেছি, তা বোধ করি সারা জীবনেও ভুলব না। যাদের কাছে জেঠিমা, কাকীমা, দিদি ব’লে হাসিমুখে ছুটে যাই, তারা যে কেন আমাদের ওপর এমন বিরূপ, কেন তাঁদের ব্যবহার এত নিষ্ঠুর, ভেবেই পাইনে এর কোনো কারণ। আমরা তো আলাদা থাকি, আমাদের খরচে আমাদের রান্না হয়, ওঁদের তো কোনোই অসুবিধের মধ্যে আমরা ফেলিনি, তবু কেন বাড়িসুদ্ধু লোকের আমাদের ওপর এত রাগ?
আমার বাবার আপন ভাই নেই, ওঁরা হলেন খুড়তুত-জাঠতুত ভাই। জ্যাঠামশায়ের অবস্থা খুবই ভালো–পাটের বড় ব্যবসা আছে, দুই ছেলে গদিতে কাজ দেখে, ছোট একটি ছেলে এখানকার স্কুলে পড়ে, আর একটি মেয়ে ছিল, সে আমাদের আসবার আগে বসন্ত হয়ে মারা গিয়েছে। মেজকাকার তিন মেয়ে–ছেলে হয়নি, বড় মেয়ের বিয়ে হয়েচে– আর দুই মেয়ে ছোট। ছোটকাকার বিয়ে হয়েছে বেশী দিন নয়–বৌও এখানে নেই। ছোটকাকা অত্যন্ত রাগী লোক, বাড়িতে সর্বদা ঝগড়াঝাঁটি করেন, গানবাজনার ভক্ত, ওপরের ঘরে সকাল নেই সন্ধ্যে নেই হারমোনিয়াম বাজাচ্ছেন।
জ্যাঠাইমার বয়স মায়ের চেয়ে বেশী, কিন্তু বেশ সুন্দরী–একটু বেশী মোটাসোটা। গায়ে ভারী ভারী সোনার গহনা। এঁর বিয়ের আগে নাকি জ্যাঠামশায়ের অবস্থা ছিল খারাপ–তারপর জ্যাঠাইমা এ বাড়িতে বধূরূপে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সংসারে উন্নতিরও সূত্রপাত। প্রতিবেশীরা খোশামোদ ক’রে বলে–আমার সামনেই আমি কতবার শুনেচি– তোমার মত ভাগ্যিমানী ক’জন আছে বড়-বৌ? এদের কি-ই বা ছিল, তুমি এলে আর সংসার সব দিক থেকে উথলে উঠলো, কপাল বলে একেই বটে! সামনে বলা নয়–এমন মন আজকাল ক’জনের বা আছে? দেওয়ায়-থোওয়ায়, খাওয়ানোয়-মাখানোয়–আমার কাছে বাপু হক কথা।
মেজখুড়ীমা ওর মধ্যে ভালো লোক। কিন্তু তিনি কারুর স্বপক্ষে কথা বলতে সাহস করেন না, তাঁর ভাল করবার ক্ষমতা নেই, মন্দ করবারও না। মেজকাকা তেমন কিছু রোজগার করেন না, কাজেই মেজখুড়ীমার কোনো কথা এ বাড়িতে খাটে না।
বছরখানেক কেটে গেল। বাবা কোথাও চাকরি পেলেন না। কত জায়গায় হাঁটাহাঁটি করলেন, শুকনো মুখে কতবার বাড়ি ফিরলেন। হাতে যা পয়সা ছিল ক্রমে ক্রমে ফুরিয়ে এল।
সকালে আমরা বাড়ির সামনে বেলতলায় খেলছিলাম। সীতা বাড়ির ভেতর থেকে বার হয়ে এল, আমি বললুম-চা হয়েছে সীতা?
সীতা মুখ গম্ভীর করে বললে––চা আর হবে না। মা বলেছে চা-চিনির পয়সা কোথায় যে চা হবে?
কথাটা আমার বিশ্বাস হ’ল না, সীতার চালাকি আমি যেন ধরে ফেলেছি, এই রকম সুরে তার দিকে চেয়ে হাসিমুখে বললুম,–যাঃ, তুই বুঝি খেয়ে এলি!
চা-বাগানে আমাদের জন্ম, সকালে উঠে চা খাওয়ার অভ্যাস আমাদের জন্মগত, চা না খেতে পাওয়ার অবস্থা আমরা কল্পনাই করতে পারিনে।
সীতা বললে–না দাদা, সত্যি, তুমি দেখে এসো–চা হচ্ছে না। তারপর বিজ্ঞের সুরে বললে–বাবার যে চাকরি হচ্চে না, মা বলছিল দু-দিন পরে আমাদের ভাতই জুটবে না। তো চা!..আমরা এখন গরিব হয়ে গিয়েছি যে।
সীতার কথায় আমাদের দারিদ্র্যের রূপটি নূতনতর মূর্তিতে আমার চোখের সামনে ফুটল। জানতুম যে আমরা গরিব হয়ে গিয়েছি, পরের বাড়িতে পরের মুখ চেয়ে থাকি, ময়লা বিছানায় শুই, জলখাবার খেতে পাইনে, আমাদের কারুর কাছে মান নেই সবই জানি। কিন্তু এ সবেও নিজেদের দারিদ্র্যের স্বরূপটি তেমন করে বুঝিনি, আজ সকালে চা না খেতে পেয়ে সেটা যেমন করে বুঝলুম।
বিকেলের দিকে বাবা দেখি পথ বেয়ে কোথা থেকে বাড়িতে আসছেন। আমায় দেখে বললেন–শোন জিতু, চল শিমুলের তুলো কুড়িয়ে আনিগে–
আমি শিমুল তুলোর গাছ এই দেশে এসে প্রথম দেখেছি-গাছে তুলো হয় বইয়ে পড়লেও চোখে দেখেছি এখানে এসে এই বৈশাখ মাসে। আমার ভারি মজা লাগল– উৎসাহ ও খুশির সুরে বললুম–শিমুল তুলো? কোথায় বাবা?…চলো যাই–সীতাকে ডাকবো?
বাবা বললেন–ডাক ডাক, সবাইকে ডাক-চল আমরা যাই—
বাবাও আমার পেছনে পেছনে বাড়ি ঢুকলেন। পরের দিন ষষ্ঠী ও দাদার জন্মবার। মা কোথা থেকে খানিকটা দুধ যোগাড় করে রান্নাঘরের দাওয়ায় উনুনে বসে বসে ক্ষীরের পুতুল গড়ছিলেন–বাবার স্বর শুনেই মুখ তুলে চেয়ে এক চমক বাবার দিকে দেখেই একবার চকিত দৃষ্টিতে ওপরে জ্যাঠাইমাদের বারান্দার দিকে কি জন্যে চাইলেন–তারপর পুতুল-গড়া ফেলে তাড়াতাড়ি উঠে এসে বাবার হাত ধরে ঘরের মধ্যে নিয়ে গেলেন। আমার দিকে ফিরে বললেন–যা জিতু, বাইরে খেলা করগে যা–
আমি অবাক হয়ে গেলুম। বলতে যাচ্ছিলাম, মা, বাবা যে শিমুল তুলো কুড়োবার– কিন্তু মার মুখের দিকে চেয়ে আমার মুখ দিয়ে কথা বার হ’ল না। একটা কিছু হয়েছে যেন–কিন্তু কি হয়েছে আমি বুঝলাম না। বাবা মদ খেয়ে আসেননি নিশ্চয়–মদ খেলে আমরা বুঝতে পারি–খুব ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছি, দেখলেই বুঝি। তবে বাবার কি হল?
অবাক হয়ে বাইরে চলে এলুম।
এখানকার স্কুলে আমি ভর্তি হয়েছি, কিন্তু দাদা আর পড়তে চাইলে না বলে তাকে ভর্তি করা হয়নি। প্রথম কয় মাস মাইনের জন্যে মাস্টার মশায়ের তাগাদার চোটে আমার চোখে জল আসত–সাড়ে ন’ আনা পয়সা মাইনে–তাও বাড়িতে চাইলে কারুর কাছে পাইনে, বাবার মুখের দিকে চেয়ে বাবার কাছে তাগাদা করতে মন সরে না।
শনিবার, সকালে স্কুলের ছুটি হবে। স্কুলের কেরানী রামবাবু একখানা খাতা নিয়ে আমাদের ক্লাসে ঢুকে মাইনের তাগাদা শুরু করলেন। আমার মাইনে বাকি দু-মাসের– আমায় ক্লাস থেকে উঠিয়ে দিয়ে বললেন–বাড়ি গিয়ে মাইনে নিয়ে এসো খোকা, নইলে আর ক্লাসে বসতে দেবো না কাল থেকে। আমার ভারি লজ্জা হ’ল–দুঃখ তো হ’লই। আড়ালে ডেকে বললেই তো পারতেন রামবাবু, ক্লাসে সকলের সামনে–ভারি–
দুপুরে রোদ ঝাঁ-ঝাঁ করছে। স্কুলের বাইরে একটা নিমগাছ। ভারি সুন্দর নিমফুলের ঘন গন্ধটা। সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবলুম কি করা যায়। মাকে বলব বাড়ি গিয়ে? কিন্তু জানি মায়ের হাতে কিছু নেই, এখুনি পাড়ায় ধার করতে বেরুবে, পাবে কি না পাবে, ছোট মুখ করে বাড়ি ফিরবে–ওতে আমার মনে বড় লাগে।
হঠাৎ আমি অবাক হয়ে পথের ওপারে চেয়ে রইলুম–ওপারে সামু নাপিতের মুদিখানার দোকানটা আর নেই, পাশেই সে ফিতে-ঘুন্সির দোকানটাও নেই, তার পাশের জামার দোকানটাও নেই–একটা খুব বড় মাঠ, মাঠের ধারে বড় বড় বাঁশগাছের মত কি গাছের সারি, কিন্তু বাঁশগাছ নয়। দুপুরবেলা নয়, বোধ হয় যেন রাত্রি–জ্যোৎস্না রাত্রি– দূরে সাদা রঙের একটা অদ্ভুত গড়নের বাড়ি, মন্দিরও হতে পারে।
নিমগাছের গুঁড়িটাতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছিলুম, সাগ্রহে সামনের দিকে ঝুঁকে ভাল দেখতে পাওয়া গেল, তখনো তাই আছে জ্যোৎস্নাভরা একটা মাঠ, কি গাছের সারি– দূরের সাদা বাড়িটা। দু মিনিট…পাঁচ মিনিট। তাড়াতাড়ি চোখ মুছলাম, আবার চাইলুম– এখনও অবিকল তাই। একেবারে এত স্পষ্ট, গাছের পাতাগুলো যেন গুনতে পারি, পাখিদের ডানার সব রঙ বেশ ধরতে পারি।
তার পরেই আবার কিছু নেই, খানিকক্ষণ সব শূন্য–তা পরেই সামু নাপিতের দোকান, পাশেই ফিতে-ঘুন্সির দোকান।
বাড়ি চলে এলুম। যখনই আমি এই রকম দেখি, তখন আমার গা কেমন করে–হাতে পায়ে যেন জোর নেই এমনি হয়। মাথা যেন হালকা মনে হয়। কেন এমন হয় আমার? কেন আমি এ-সব দেখি? কাউকে এ কথা বলতে পারিনে, মা, বাবা, দাদা, সীতা, কাউকে নয়। আমার এমন কোনো বন্ধু বা সহপাঠী নেই, যাকে আমি বিশ্বাস করে সব কথা খুলে বলি। আমার মনে মনে যেন কে বলে–এরা এ-সব বুঝবে না। বন্ধুরা হয়ত হেসে উঠবে, কি ওই নিয়ে ঠাট্টা করবে।
ওবেলা খেয়ে যাইনি। রান্নাঘরে ভাত খেতে গিয়ে দেখি শুধু সিমভাতে আর কুমড়োর ডাঁটা চচ্চড়ি। আমি ডাঁটা খাইনে–সিম যদি বা খাই সিমভাতে একেবারেই মুখে ভাল লাগে না। মাকে রাগ করে বললুম–ও দিয়ে ভাত খাবো কি করে? সিমভাতে দিলে কেন? সিমভাতে আমি খাই কখনও?
কিন্তু মাকে যখন আমি বকছিলুম আমার মনে তখন মায়ের ওপর রাগ ছিল না। আমি জানি আমাদের ভাল খাওয়াতে মায়ের যত্নের ক্রটি কোনো দিন নেই, কিন্তু এখন মা অক্ষম, অসহায়–হাতে পয়সা নেই, ইচ্ছে থাকলেও নিরুপায়। মায়ের এই বর্তমান অক্ষমতার দরুন মায়ের ওপর যে করুণা সেটাই দেখা দিল রাগে পরিবর্তিত হয়ে। চেয়ে দেখি মায়ের চোখে জল। মনে হ’ল এ সেই মা-চা-বাগানে থাকতে মিস নর্টনের কাছ থেকে আমাদের খাওয়ানোর জন্যে কেক তৈরি করবার নিয়ম শিখে বাজার থেকে ঘি ময়দা কিশমিশ ডিম চিনি সব আনিয়ে সারা বিকেল ধরে পরিশ্রম করে কতকগুলো স্বাদগন্ধহীন নিরেট ময়দার ঢিপি বানিয়ে বাবার কাছে ও পরদিন মিস নর্টনের কাছে হাস্যাস্পদ হয়েছিলেন! তার পর অবিশ্যি মিস নর্টন ভাল করে হাতে ধরে শেখায় এবং মা ইদানীং খুব ভাল কেকই গড়তে পারতেন।
মা বাংলা দেশের পাড়াগাঁয়ের ধরন-ধারণ, রান্না, আচার-ব্যবহার ভাল জানতেন না– অল্প বয়সে বিয়ে হয়ে চা-বাগানে চলে গিয়েছিলেন, সেখানে একা একা কাটিয়েছেন। চিরকাল সমাজের বাইরে–পাড়াগাঁয়ের ব্রত-নেম পুজোআচ্চা আচার এ-সব তেমন জানা ছিল না। ওদের এই ঘোর আচারী সংসারে এসে পড়ে আলাদা থাকলেও মাকে কথা সহ্য করতে হয়েছে কম নয়। পয়সা থাকলে যেটা হয়ে দাঁড়াত গুণ–হাত খালি থাকাতে সেটা হয়ে দাঁড়িয়েছিল ঠাট্টা, বিদ্রূপ, শ্লেষের ব্যাপার–জংলীপনা খিরিস্টানি বা বিবিয়ানা। মার সহ্যগুণ ছিল অসাধারণ, মুখ বুজে সব সহ্য করতেন, কোনোদিন কথাটিও বলেননি। ভয়ে ভয়ে ওদের চালচলন, আচার-ব্যবহার শিখবার চেষ্টা করতেন–নকল করতে যেতেন– তাতে ফল অনেক সময়ে হ’ত উল্টো।
আরও মাসকতক কেটে গেল। সেই ক-মাসে আমাদের যা অবস্থা হয়ে দাঁড়ালো, জীবনে ভাবিওনি কোনো দিন যে অত কষ্টের মধ্যে পড়তে হবে। দু-বেলা ভাত খেতে আমরা ভুলে গেলাম। স্কুল থেকে এসে বেলা তিনটের সময় খেয়ে রাত্রে কিছু খাওয়ার ইচ্ছেও হত না। ভাত খেয়ে স্কুলে যাওয়াটা ঘটত না প্রায়ই, অত সকালে মা চালের যোগাড় করতে পারতেন না, সেটা প্রায়ই ধার করে নিয়ে আসতে হ’ত। সব সময় হাতে পয়সা থাকত না–এর মানে আমাদের চা-বাগানের শৌখিন জিনিসপত্র, দেরাজ, বাক্স– এইসব বেচে চলছিল–সব সময়ে তার খদ্দের জুটতো না। মা বৌমানুষ, বিশেষত এটা অপরিচিত স্থান, নিজের শ্বশুরবাড়ি হলেও এর সঙ্গে এত কাল কোনো সম্পর্কই ছিল না– কিন্তু মা ও সব মানতেন না, লজ্জা করে বাড়ি বসে থাকলে তাঁর চলত না, যেদিন ঘরে কিছু নেই, পাড়ায় বেরিয়ে যেতেন, দু-একটা জিনিস বেচবার কি বন্ধক দেবার চেষ্টা করতেন পাড়ার মেয়েদের কাছে। প্রায়ই শৌখীন জিনিস, হয়ত একটা ভাল কাচের পুতুল, কি গালার খেলনা, চন্দনকাঠের হাতপাখা এইসব–সেলাইয়ের কলটা ছোট কাকীমা সিকি দামে কিনেছিলেন। বাবার গায়ের ভারী পুরু পশমী ওভারকোটটা সরকাররা কিনে নিয়েছিল আট টাকায়। মোটে এক বছর আগে পঞ্চাশ টাকা দিয়ে বাবা সেটা তৈরি করিয়েছিলেন।
চাল না হয় একরকম করে জুটলো, কিন্তু আমাদের পরনের কাপড়ের দুর্দশা ক্রমেই বেড়ে উঠছিল। আমাদের সবারই একখানা করে কাপড়ে এসে ঠেকেছে–তাও ছেঁড়া, আমার কাপড়খানা তো তিন জায়গায় সেলাই। সীতা বলত, তুই বড় কাপড় ছিঁড়িস দাদা! কিন্তু আমার দোষ কি? পুরোনো কাপড়, একটু জোরে লাফালাফি করলেই ছিঁড়ে যেত, মা অমনি সেলাই করতে বসে যেতেন।
বাবা আজকাল কেমন হয়ে গেছেন, তেমনি কথাবার্তা বলেন না–বাড়িতেও থাকেন না প্রায়ই। তাঁকে পাওয়াই যায় না যে কাপড়ের কথা বলি। তা ছাড়া বাবার মুখের দিকে চেয়ে কোনো কথা বলতেও ইচ্ছে যায় না। তিনি সব সময়ই চাকরির চেষ্টায় এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ান, কিন্তু কোথাও এ পর্যন্ত কিছু জোটেনি। মাস-দুই একটা গোলদারি দোকানে খাতাপত্র লেখবার চাকরি পেয়েছিলেন, কিন্তু এখন আর সে চাকরি নেই–সেজ জ্যাঠামশায়ের ছেলে নবীন বলছিল, নাকি মদ খেয়ে গেছে। কিন্তু এখানে এসে বাবা একদিনও মদ খেয়েছেন বলে আমার মনে হয় না, বাবা মদ খেলেই উৎপাত করেন। আমরা ভাল করেই জানি, কিন্তু এখানে এসে পর্যন্ত দেখচি বাবার মত শান্ত মানুষটি আর পৃথিবীতে নেই। এত শান্ত, এত ভাল মানুষ স্নেহময় লোকটি মদ খেলে কি হয়েই যেতেন! চা-বাগানের সে-সব রাতের কীর্তি মনে হলেও ভয় করে।
রবিবার। আমার স্কুল নেই, আমি সারাদিন বসে বসে ম্যাজেন্টা গুলে রঙ তৈরি করেছি, দু-তিনটে শিশিতে ভর্তি করে রেখেছি, সীতার পাঁচ-ছখানা পুতুলের কাপড় রঙে ছুপিয়ে দিয়েছি–ক্লাসের একটা ছেলের কাছ থেকে অনেকখানি ম্যাজেন্টার গুঁড়ো চেয়ে নিয়েছিলুম।
সন্ধ্যার একটু পরেই খেয়ে শুয়েচি, কত রাত্রে যেন ঘুম ভেঙে গেল–একটু অবাক হয়ে চেয়ে দেখি আমাদের ঘরের দোরে জ্যাঠাইমা, আমার খুড়তুতো জ্যাঠতুতো ভাইবোনের দল, ছোট কাকা–সবাই দাঁড়িয়ে। মা কাঁদছেন–সীতা বিছানায় সবে ঘুম ভেঙে উঠে বসে চোখ মুছছে। আমার জ্যাঠতুতো ভাই হেসে বললেন–ঐ দ্যাখ তোর বাবা কি করচে! চেয়ে দেখি ঘরের কোণে খাটে বাবা তিনটে বালিশের তুলো ছিঁড়ে পুঁটুলি বাঁধচেন। তুলোতে বাবার চোখমুখ, মাথার চুল, সারা গা এক অদ্ভুত রকম হয়েছে দেখতে। আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলুম–কি হয়েছে বাবা?
বাবা বললেন–চা-বাগানে আবার চাকরি পেয়েছি–ছোট সাহেব তার করেচে সকালের গাড়িতে যাব কিনা তাই পুঁটুলিগুলো বেঁধেছেঁদে এখন না রাখলে–কটা বাজল রে খোকা?
আমার বয়স কম হলেও আমার বুঝতে দেরি হ’ল না যে এবার বাবা মাতাল হননি। এ অন্য জিনিস। তার চেয়েও গুরুতর কিছু। ঘরের দৃশ্যটা আমার মনে চিরকালের মতো একটা ছাপ দিয়ে দিয়েছিল–জীবনে কখনও ভুলিনি–চোখ বুজলেই উত্তরজীবনে আবার সে-রাত্রির দৃশ্যটা মনে এসেছে। একটা মাত্র কেরোসিনের টেমি জ্বলচে ঘরে–তারই রাঙা ক্ষীণ আলোয় ঘরের কোণে বাবার তুলো-মাখা চেহারা-মাথায় মুখে কানে পিঠে সর্বাঙ্গে ছেঁড়া বালিশের লালচে পুরানো বিচিওয়ালা তুলো, মেঝেতে বসে মা কাঁদচেন–দরজার কাছে কৌতুক দেখতে খুড়ীমা জ্যাঠাইমারা জড়ো হয়েছেন–খুড়তুতো ভাই-বোনেরা হাসচে …দাদাকে ঘরের মধ্যে দেখতে পেলাম না, বোধ হয় বাইরে কোথাও গিয়ে থাকবে।
পরদিন সকালে আমাদের ঘরের সামনে উঠানে দলে দলে লোক জড়ো হতে লাগল। এদের মুখে শুনে প্রথম বুঝলাম বাবা পাগল হয়ে গিয়েছেন। সংসারের কষ্ট, মেয়ের বিয়ের ভাবনা, পরের বাড়ির এই যন্ত্রণা–এই সব দিনরাত ভেবে ভেবে বাবার মাথা গিয়েছে বিগড়ে। অবিশ্যি এ-সব কারণ অনুমান করেছিলুম বড় হলে, অনেক পরে।
বেলা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লোকের ভিড় বাড়তে লাগল, যারা কোনো দিন এর আগে বাবার সঙ্গে মৌখিক ভদ্র আলাপটা করতেও আসেনি তারা মজা দেখতে আসতে লাগল দলে দলে।
বাবার মূর্তি হয়েছে দেখতে অদ্ভুত। রাত্রে না ঘুমিয়ে চোখ বসে গিয়েছে–চোখের কোলে কালি মেড়ে দিয়েছে যেন। সর্বাঙ্গে তুলো মেখে বাবা সেই রাতের বিছানার ওপরেই বসে আপনমনে কি বকছেন। ছেলেপিলের দল এপাড়া-ওপাড়া থেকে এসেছে। তারা ঘরের দোরে ভিড় করে দাঁড়িয়ে। কেউ বা উঁকি মেরে দেখচে-হাসাহাসি করছে। আমাদের সঙ্গে পড়ে এই পাড়ার নবীন বাঁড়ুয্যের ছেলে শান্টু–সে একবার উঁকি মেরে দেখতেই বাবা তাকে কি একটা ধমক দিয়ে উঠলেন। সে ভান-করা ভয়ের সুরে বলে উঠল–ও বাবা! মারবে নাকি? বলেই পিছিয়ে এল। ছেলের দলের মধ্যে একটা হাসির ঢেউ পড়ে গেল।
একজন বললে–আবার কি রকম ইংরিজি বলছে দ্যাখ—
আমি ও সীতা কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে আছি। আমরা কেউ কোন কথা বলচি নে।
আর একটু বেলা হলে জ্যাঠামশায় কি পরামর্শ করলেন সব লোকজনের সঙ্গে– আমার মাকে উদ্দেশ করে বললেন–বৌমা, সবই তো দেখতে পাচ্চ–তোমাদের কপাল ছাড়া আর কি বলব। ভূষণকে এখন বেঁধে রাখতে হবে–সেই মতই সবাই করেছেন। ছেলেপিলের বাড়ি-পাড়ার ভেতরকার কাণ্ড-–এরকম অবস্থায় কখন কি করে বসে, তা বলা যায় না…তা তোমায় একবার বলাটা দরকার তাই–
আমার মনে বড় কষ্ট হ’ল–বাবাকে বাঁধবে কেন? বাবা তো এক বকুনি ছাড়া আর কারুর কিছু অনিষ্ট করতে যাচ্ছেন না–কেন তবে—
আমার মনের ভাষা বাক্য খুঁজে পেলে না প্রকাশের–মনেই রয়ে গেল। বাবাকে সবাই মিলে বাঁধলে! আহা, কি কষে কষেই বাঁধলে। অন্য দড়ি কোথাও পাওয়া গেল না বা ছিল না–জ্যাঠামশায়দের খিড়কি-পুকুর ধারের গোয়াল-বাড়ি থেকে গরু বাঁধবার দড়ি নিয়ে এল–তাই দিয়ে বাঁধা হ’ল।
আমার মনে হ’ল অতটা জোর করে বাবাকে বাঁধবার দরকার কি! বাবার হাতের শির দড়ির মতো ফুলে উঠেছে যে। সেজ কাকাকে চুপিচুপি বললুম–কাকাবাবু, বাবার হাতে লাগছে, অত করে বেঁধেচে কেন? বলুন না ওদের?
কাকা সে-কথা জ্যাঠামশায়কে ও নিতাইয়ের বাবাকে বলতে তাঁরা বললেন–তুমিও কি খেপলে নাকি রমেশ? হাত আলগা থাকবে পাগলের?…তা হলে পা খুলতে কতক্ষণ– তারপরে আমার দিকে চেয়ে জ্যাঠামশায় বললেন–যাও জিতু বাবা–তুমি বাড়ির ভেতরে যাও–নয়তো এখন বাইরে গিয়ে বসো।
আবার বাবার হাতের দিকে চেয়ে দেখলুম–দড়ির দাগ কেটে বসে গিয়েছে বাবার হাতে। সেই রকম তুলোমাখা অদ্ভুত মূর্তি!…
বাইরে গিয়ে আমি একা গাঁয়ের পেছনের মাঠের দিকে চলে গেলুম–একটা বড় তেঁতুল গাছের তলায় সারা দুপুর ও বিকেল চুপ করে বসে রইলুম।
দিন কতক এই ভাবে কাটল। তারপর পাড়ার দু-পাঁচজন লোকে এসে জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে কি পরামর্শ করলে। বাবাকে কোথায় তারা নিয়ে গেল, সবাই বললে কলকাতায় হাসপাতালে নিয়ে গেছে। তারা ফিরেও এল, শুনলুম, বাবাকে নাকি হাসপাতালে ভর্তি করে নিয়েছে। শীগগিরই সেরে বাড়ি ফিরবেন। আমরা আশ্বস্ত হলুম।
দশ-বারো দিন পরে একদিন বিকেলের দিকে আমি ও সীতা পথে খেলা করছি, এমন সময় সীতা বললে–ঐ যে বাবা!…দূরে পথের দিকে চেয়ে দেখি বাবাই বটে। ছুটে আমরা বাড়িতে মাকে খবর দিতে গেলুম। একটু পরে বাবা বাড়ি ঢুকলেন–এক হাঁটু ধুলো, রুক্ষ চুল। ওপর থেকে জ্যাঠাইমা নেমে এলেন, কাকারা এলেন। বাবাকে দেখে সবাই চটে গেলেন। সবাই বুঝতে পারলে বাবা এখনও সারেন নি, তবে সেখান থেকে তাড়াতাড়ি চলে আসার কি দরকার?
বাবা একটু বসে থেকে বললেন, ভাত আছে? কাল ওই দিকের একটা গাঁয়ে দুপুরে দুটো খেতে দিয়েছিল, আর কিছু খাই নি সারাদিন, খিদে পেয়েছে। কলকাতা থেকে পায়ে হেঁটে আসচি-ছেলেপিলে ছেড়ে থাকতে পারলাম না–চলে এলাম।
একটু পরেই বোঝা গেল বাবা হাসপাতাল থেকে পালিয়ে এসেছেন এবং যেমন পাগল তেমনি আছেন। এবার আমাদের রাগ হ’ল–মায়ের কথা বলতে পারিনে কারণ তাঁকে রাগ প্রকাশ করতে কখনও দেখি নি–কিন্তু আমি সীতা দাদা তিন ভাইবোনে খুব চটলাম।
আমাদের চটবার কারণও আছে–খুব সঙ্গত কারণই আছে। আমাদের প্রাণ এখানে অতিষ্ঠ হয়ে উঠছে। বাবা আবার পুরোমাত্রায় পাগল হয়ে উঠলেন–তিনি দিনরাত বসে বসে বকেন আর কেবল খেতে চান। মা দুটি বাসি মুড়ি, কোনো দিন বা ভিজেচাল, কোনো দিন শুধু একটু গুড়–এই খেতে দেন। তাও সব দিন বা সব সময় জোটানো কষ্টকর। আমরা দুপুরে খাই তো রাতে আর কিছু খেতে পাইনে–নয়ত সারাদিন পরে হয়ত সন্ধ্যার সময় খাই। মা কোথা থেকে চাল যোগাড় করে আনেন আমরা জানিনে– কখনও জিজ্ঞেসও করিনি। কিন্তু বাড়িতে আর আমাদের তিষ্ঠুবার জো নেই। বাড়িসুদ্ধ লোক আমাদের ওপর বিরূপ–দু-বেলা তাদের অনাদর আর মুখনাড়া সহ্য করা আমাদের অসহ্য হয়ে উঠেছে। চা-বাগানের দিনগুলোর কথা মনে হয়, সেখানে আমাদের কোন কষ্ট ছিল না–অবস্থা ছিল অত্যন্ত সচ্ছল, ছেলেবেলায় সীতাকে ভুটিয়া চাকরে নিয়ে বেড়াত আর থাপা মানুষ করেছিল আমাদের। ছ-বছর বয়স পর্যন্ত আমি থাপার কাঁধে উঠে বেড়াতাম মনে আছে। আমাদের এই বর্তমান দুরবস্থার জন্য বাবাকে আমরা মনে মনে দায়ী করেছি। বাবা কেন আবার ভাল হয়ে সেরে উঠুন না? তা হলে আর আমাদের কোনো দুঃখই থাকে না। কেন বাবা ওরকম পাগলামি করেন? ওতে লজ্জায় যে ঘরে বাইরে আমাদের মুখ দেখাবার জো নেই।
সেদিন সকালে সেজ খুড়ীমা এসে আমাদের সঙ্গে খুব ঝগড়া বাধালেন। মেজ খুড়ীমাও এসে যোগ দিলেন। তাঁদের বাগানে বাতাবী নেবু গাছ থেকে চার-পাঁচটা পাকা নেবু চুরি গিয়েছে। খুড়ীমা এসে মাকে বললেন–এ আমাদেরই কাজ–আমরা খেতে পাইনে, আমরাই নেবু চুরি করে ঘরে রেখেছি। তাঁরা সবাই মিলে আমাদের ঘর খানাতল্লাসী করতে চাইলেন। মা বললেন–এসে দেখে যান মেজদি, আমার ঘরে তো লোহার সিন্দুক নেই যে সেখানে আমার ছেলেমেয়েরা নেবু লুকিয়ে রেখেছে…এসে দেখুন—
শেষ পর্যন্ত বাবা ঘরে আছেন বলে তাঁরা ঘরে ঢুকতে পারলেন না, কিন্তু সবাই ধরে নিলে যে নেবু আমাদের ঘরে আছে, খানাতল্লাসী করলেই বেড়িয়ে পড়ত। খুব ঝগড়াঝাঁটি হ’ল–তবে সেটা হ’ল একতরফা, কারণ এ-পক্ষ থেকে তার জবাব কেউ দিল না।
জ্যাঠাইমা এ বাড়ির কর্ত্তী, তাঁকে সবাই মেনে চলে, ভয়ও করে। তিনি এসে বললেন–হয় তোমরা বাড়ি থেকে চলে যাও, নয়ত ঘরের ভাড়া দাও।
সীতা এসে আমাকে বলল–জ্যাঠাইমা এবার বাড়িতে আর থাকতে দেবে না, না দেবে না দেবে, আমরা কোথাও চলে যাই চল দাদা।
দিন-দুই পরে জ্যাঠামশাইদের সঙ্গে কি একটা মিটমাট হ’ল। ঠিক হ’ল যে দাদা চাকরির যোগাড় করতে কলকাতায় যাবে, ঘরে আমরা আপাতত কিছুকাল থাকতে পাব। কিন্তু বাড়ির ও পাড়ার সবাই বললে পাগলাটাকে আর বাড়ি রেখে দরকার নেই, ওকে জলেজঙ্গলে কোথাও ছেড়ে দিয়ে আয়।
সত্যি কথা বলতে গেলে বাবার উপর আমাদের কারুর আর মমতা ছিল না। বাবার চেহারাও হয়ে উঠেছে অদ্ভুত। একমাথা লম্বা চুল জটা পাকিয়ে গিয়েছে–আগে আগে মা নাইয়ে দিতেন, আজকাল বাবা কিছুতেই নাইতে চান না, কাছে যেতে দেন না, কাপড় ছাড়েন না…গায়ের গন্ধে ঘরে থাকা অসম্ভব! মা একদিনও রাত্রে ঘুমুতে পারেন না–বাবা কেবলই ফাই-ফরমাশ করেন–জল দাও পান দাও আর কেবলই বলেন খিদে পেয়েছে। কখনও বলেন চা ক’রে দাও। না পেলেই তিনি আরও ক্ষেপে ওঠেন–এক মা ছাড়া তখন আর কেউ সামলে রাখতে পারে না–আমরা তখন ঘর ছেড়ে পালিয়ে যাই, মা বুঝিয়ে-সুজিয়ে শান্ত করে চুপ করিয়ে রাখেন, নয়ত জোর করে বালিশে শুইয়ে দিয়ে বাতাস করেন, পা টিপে দেন–কিন্তু তাতে বাবা সাময়িক চুপ করে থাকেন বটে, ঘুমোন না। পাগল হয়ে পর্যন্ত বোধ হয় একদিনও বাবার ঘুম হয় নি। নিজেও ঘুমুবেন না কাউকে ঘুমুতেও দেবেন না–সারারাত চীৎকার, বকুনি, ইংরেজি বক্তৃতা, গান–এই সব করবেন। সবাই বলে, ঘুমুলে নাকি বাবার রোগ সেরে যেত।
শেষ পর্যন্ত হয়ত মা মত দিয়েছিলেন, হয়ত বলেছিলেন–তোমরা যা ভাল বোঝ করো বাপু। মোটের ওপর একদিন স্কুলে দাদা এসে বললে–সকাল সকাল বাড়ি চল আজ জিতু–আজ বাবাকে আড়াগাঁয়ে জলার ধারে ছেড়ে দিয়ে আসতে হবে–তুই, আমি, নিতাই, সিধু আর মেজকাকা যাব।
একটু পরে আমি ছুটি নিয়ে বেরুলাম। গিয়ে দেখি মা দালানে বসে কাঁদছেন, আমরা যাবার আগেই নিতাই এসে বাবাকে নিয়ে গিয়েছে। আমরা খানিক দূরে গিয়ে ওদের নাগাল পেলাম–পাড়ার চার-পাঁচজন ছেলে সঙ্গে আছে, মধ্যিখানে বাবা। ওরা বাবার সঙ্গে বাজে বকছে–শিকারের গল্প করছে, বাবাও খুব বকচেন। নিতাই আমাকে বাবার সামনে যেতে বারণ করাতে আমি আর দাদা পেছনেই রইলাম। ওরা মাঠের রাস্তা ধরে অনেক দূর গেল, একটা বড় বাগান পার হ’ল, বিকেলের পড়ন্ত রোদে ঘেমে আমরা সবাই নেয়ে উঠলাম। রোদ যখন পড়ে গিয়েছে তখন একটা বড় বিলের ধারে সবাই এসে পৌঁছলাম। নিতাই বললে–এই তো আড়াগাঁয়ের জলা-চল, বিলের ওপারে নিয়ে যাই–ওই হোগলা বনের মধ্যে ছেড়ে দিলে আর পথ খুঁজে পাবে না রাত্তিরে। আমরা কেউ ওপারে গেলুম না।—গেল শুধু সিধু আর নিতাই। খানিকটা পরে ওরা ফিরে এসে বললে, চল পালাই– তোর বাবাকে একটা সিগারেট খেতে দিয়ে এসেছি–বসে বসে টানচে। চল ছুটে পালাই–
সবাই মিলে দৌড় দিলাম। দাদা তেমন ছুটতে পারে না, কেবলই পেছনে পড়তে লাগল। সন্ধ্যার ঘোরে জলা আর জঙ্গলের মধ্যে পথ খুঁজে পাওয়া যায় না–এক প্রহর রাত হয়ে গেল বাড়িতে পৌঁছুতে। কিন্তু তিন দিনের দিন বাবা আবার বাড়ি এসে হাজির। চেহারার দিকে আর তাকানো যায় না–কাদামাখা ধুলোমাখা অতি বিকট চেহারা। বেল না কি ভেঙে খেয়েছেন–সারা মুখে গালে বেলের আঠা ও শাঁস মাখানো। মা নাইয়ে ধুইয়ে ভাত খেতে দিলেন, বাবা খাওয়া-দাওয়ার পর সেই যে বিছানা নিলেন, দু’দিন চার দিন ক’রে ক্রমে পনের দিন কেটে গেল, বাবা আর বিছানা থেকে উঠলেন না। লোকটা যে কেন বিছানা ছেড়ে ওঠে না–তার কি হয়েছে–এ কথা কেউ কোনোদিন জিজ্ঞেসও করলে না। মা যেদিন যা জোটে খেতে দেন, মাঝে মাঝে নাইয়ে দেন–পাড়ার কোন লোকে উঁকি মেরেও দেখে গেল না।
জ্যাঠামশাইরা হতাশ হয়ে গিয়েছেন। তাঁরা আর আমাদের সঙ্গে কথা কন না, তাঁদের ঘরে-দোরে ওঠা আমাদের বন্ধ। আমরা কথা বলি চুপি চুপি, চলি পা টিপেটিপে চোরের মত, বেড়াই মহা অপরাধীর মত–পাছে ওঁরা রাগ করেন, বিরক্ত হন, আবার ঘর থেকে তাড়িয়ে দিতে আসেন।
একদিন না খেয়ে স্কুলে পড়তে গিয়েছি–অন্য দুদিনের মত টিফিনের সময় সীতা খাবার জন্যে ডাকতে এল না। প্রায়ই আমি না খেয়ে স্কুলে আসতাম, কারণ অত সকালে মা রান্না করতে পারতেন না–রান্না শুধু করলেই হ’ল না, তার যোগাড় করাও তো চাই। মা কোথা থেকে কি যোগাড় করতেন, কি করে সংসার চালাতেন, তিনিই জানেন। আমি কখনও তা নিয়ে ভাবি নি। আমি ক্ষুধাতুর অবস্থায় বেলা একটা পর্যন্ত ক্লাসের কাজ করে যেতাম আর ঘন ঘন পথের দিকে চাইতাম এবং রোজই একটার টিফিনের সময় সীতা এসে ডাক দিত–দাদা, ভাত হয়েছে খাবে এসো।
এ-দিন কিন্তু একটা বেজে গেল, দুটো বেজে গেল, সীতা এল না। ক্লাসের কাজে আমার আর মন নেই–আমি জানলা দিয়ে ঘন ঘন বাইরে পথের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখচি। আরও আধ ঘণ্টা কেটে গেল, বেলা আড়াইটা। এমন সময় কলুদের দোকানঘরের কাছে সীতাকে আসতে দেখতে পেলাম। আমার ভারি রাগ হ’ল, অভিমানও হ’ল। নিজেরা সব খেয়ে দেয়ে পেট ঠাণ্ডা করে এখন আসছেন।
মাস্টারের কাছে ছুটি নিয়ে তাড়াতাড়ি বাইরে গেলাম। সীতার দিকে চেয়ে দূর থেকে বললাম–বেশ দেখচি–আমার বুঝি আর খিদে-তেষ্টা পায় না? কটা বেজেছে জানিস?
সীতা বললে–বাড়ি এস ছোড়দা, তোমার বইপত্র নিয়ে ছুটি করে এস গে—
আমি বললাম–কেন রে?
সীতা বললে–এস না, ছুটির আর দেরি বা কত? তিনটে বেজেচে–
আমার মনে হ’ল একটা কি যেন হয়েছে। স্কুল থেকে বেরিয়ে একটু দূর এসেই সীতা বললে–বাবা মারা গিয়েচে ছোড়দা।
আমি থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম–সীতার মুখের দিকে চেয়ে সে যে মিথ্যে কথা বলছে এমন মনে হল না। বললাম–কখন?
সীতা বললে–বেলা একটার সময়—
নিজের অজ্ঞাতসারে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল–নিয়ে গিয়েচে তো?
অর্থাৎ গিয়ে মৃতদেহ দেখতে না হয়। কিন্তু সীতা বললে–না, নিয়ে এখনও কেউ যায় নি। মা একা কি করবে? …জ্যাঠামশাই বাড়ি নেই–ছোট কাকা একবার এসে দেখে চলে গেলেন–আর আসেন নি। মেজকাকা পাড়ায় লোক ডাকতে গেছেন।
বাড়িতে ঢুকতেই মা বললেন–ঘরের মধ্যে আয়–মড়া ছুঁয়ে বসে থাকতে হবে, বোস এখানে।
কেউই কাঁদছে না। আমারও কান্না পেল না–বরং একটা ভয় এল–একা মড়ার কাছে কেমন ক’রে কতক্ষণ বসে থাকব না জানি!
অনেকক্ষণ পরে শুনতে পেলুম আমাদের পাড়ার কেউ মৃতদেহ নিয়ে যেতে রাজী নয়, বাবা কি রোগে মারা গেছেন কেউ জানে না, তাঁর প্রায়শ্চিত্ত করানো হয় নি মৃত্যুর পূর্বে– এ অবস্থায় কেউ সৎকার করতে রাজী নয়। প্রায়শ্চিত্ত এখন না করালে কেউ ও মড়া ছোঁবে না।
প্রায়শ্চিত্ত করাতে পাঁচ-ছ টাকা নাকি খরচ। আমাদের হাতে অত তো নেই–মা বললেন। কে যেন বললে–তা এ অবস্থায় হাতে না থাকলে লোকের কাছে চেয়ে-চিনতে আনতে হয়, কি আর করবে?
দাদাকে মা ও-পাড়ার কার কাছে পাঠালেন টাকার জন্যে। খানিকটা পরে ও-পাড়া থেকে জনকতক ষণ্ডামত লোক এল–শুনলাম তারা গালাগালি দিতে দিতে বাড়িতে ঢুকছে–এমন ছোটলোকের পাড়াও তো কখনো দেখি নি? কোথায় পাবে এরা যে প্রাচিত্তির করাবে? প্রাচিত্তির না হ’লে মড়া কি সারা দিনরাত ঘরেই পড়ে থাকবে? যত ছোটলোক সব–কোনো ভয় নেই, দেখি মড়া বার হয় কিনা।
আমি উত্তেজনার মাথায় মড়া ছুঁয়ে বসে থাকার কথা ভুলে গিয়ে তাড়াতাড়ি দোরের কাছে এসে দাঁড়ালাম। এদের মধ্যে আমি একজনকে কেবল চিনি। মাঠবাড়ির ফুটবল খেলার ময়দানে দেখেছিলাম।
ওরা নিজেরাই কোথা থেকে বাঁশ কেটে নিয়ে এল–পাট নিয়ে এসে দড়ি পাকালে, তারপর বাবাকে বার করে নিয়ে গেল–দাদা গেল সঙ্গে শ্মশানে। একটু পরে সন্ধ্যা হ’ল। সেজ খুড়ীমা এসে বললেন- মুড়ি খাবি জিতু? আমি ও সীতা মুড়ি খেয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।
তিন বছর আগেকার কথা এসব। তার পর থেকে এ বাড়িতেই আছি। জ্যাঠামশাইরা প্রথমে রাজী হন নি, দাদা ষষ্ঠীতলায় বটগাছের নীচে মুদিখানার দোকান করেছিল– সামান্য পুঁজি, আড়াই সের চিনি, পাঁচ সের ডাল, পাঁচ সের আটা, পাঁচ পোয়া ঝাল মশলা–এই নিয়ে দোকান কতদিন চলে? দাদা ছেলেমানুষ, তা ছাড়া ঘোরপেঁচ কিছু বোঝে না, একদিক থেকে সব ধারে বিক্রী করেছে, যে ধারে নিয়েচে সে আর ফিরে দোকানের পথ মাড়ায় নি। দোকান উঠে যাওয়ার পরে দাদা চাকরির চেষ্টা বেরুলো, সে তার ছোট মাথায় আমাদের সংসারের সমস্ত ভাবনা-ভার তুলে নিয়ে বাবার প্রতিনিধি রূপে আমাদের খাওয়া-পরানোর দুশ্চিন্তায় রাতে ঘুমুতো না, সারাদিন চাকরি খুঁজে বেড়াত। নস্যির কারখানায় একটা সাত টাকা মাইনের চাকরিও পেল–কিন্তু বেশী দিন রইল না, মাস-দুই পরে তারা বললে–ব্যবসার অবস্থা খারাপ, এখন লোক দরকার নেই।
সুতরাং জ্যাঠামশায়দের সংসারে মাথা গুঁজে থাকা ছাড়া আমাদের উপায় বা কি? নিতান্ত লোকে কি বলবে এই ভেবে এঁরা রাজী হয়েছেন। কিন্তু এখানে আমাদের খাপ খায় না–এখানে মাত্র যে শুধু এ বাড়িতে তা নয়, এ দেশটার সঙ্গেই খাপ খায় না। বাংলা দেশ আমাদের কারও ভাল লাগে না। আমার না, দাদার না, সীতার না, মায়েরও না। না দেশটা দেখতে ভাল, না এখানকার লোকেরা ভাল। আমাদের চোখে এ দেশ বড় নিচু, আঁটসাঁটা, ছোট বলে মনে হয়–যে-দিকেই চাই চোখ বেধে যায়, হয় ঘরবাড়িতে না-হয় বাঁশবনে আমবনে। কোথাও উঁচুনীচু নেই, একঘেয়ে সমতলভূমি, গাছপালারও বৈচিত্র্য নেই। আমাদের এ গাঁয়ের যত গাছপালা আছে, তার বেশীর ভাগ একধরনের ছোট ছোট গাছ, এর নাম বলে আশশেওড়া, তাদের পাতায় এত ধুলো যে সবুজ রঙ দিনরাত চাপা পড়ে থাকে। এখানে সব যেন দীনহীন, সব যেন ছোট মাপকাঠির মাপে গড়া।
আমাদের দিক থেকে তো গেল এই ব্যাপার। ওঁদের দিক থেকে ওঁরা আমাদের পর করে রেখেছেন এই তিন-চার বছর ধরেই। ওঁদের আপনার দলের লোক বলে এঁরা আমাদের ভাবেন না। আমরা খিরিস্টান, আচার জানিনে, হিন্দুয়ানী জানিনে-জংলী জানোয়ারের সামিল, গারো পাহাড়ী অসভ্য মানুষদের সামিল। পাহাড়ী জাতিদের সম্বন্ধে ওঁরা যে খুব বেশী জানেন তা নয়–এবং জানেন না বলেই তাদের সম্বন্ধে এঁদের ধারণা অদ্ভুত ও আজগুবী ধরনের।
এদেশে শীতকাল নেই–মাস দুই-তিন একটু ঠাণ্ডা পড়ে। তা ছাড়া সারা বছর ধরে গরম লেগেই আছে–আর কি সাংঘাতিক পরম! সে গরমের ধারণা ছিল না কোন কালে আমাদের। রাতের পর রাত ঘুম হয় না, দিনমানেও ঘামে বিছানা ভিজে যায় বলে ঘুম হয় না। গা জ্বলে, মাথার মধ্যে কেমন করে, রাত্রে যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে এক একদিন। তার ওপরে মশা। কি সুখেই লোকে এ-সব দেশে বাস করে!
.
০৪.
জ্যাঠামশাইদের বাড়ির শালগ্রামশিলার ওপর আমার ভক্তি ছিল না। ওঁদের জাঁকজমক ও পূজার সময়কার আড়ম্বরের ঘটা দেখে মন আরও বিরূপ হয়ে উঠল। আগেই বলেছি আমার মনে হ’ত, ওঁদের এই পূজা-অর্চনার ঘটার মূলে রয়েছে বৈষয়িক উন্নতির জন্য ঠাকুরের প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখানো ও ভবিষ্যতে যাতে আরও টাকাকড়ি বাড়ে সে উদ্দেশ্যে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা জানানো। তাঁকে প্রসন্ন রাখলেই এঁদের আয় বাড়বে, দেশে খাতির বাড়বে–আমার জ্যাঠাইমাকে সবাই বলবে ভাল, সংসারের লক্ষ্মী, ভাগ্যবতী–তাঁর পয়েতে এ-সব হচ্ছে, সবাই খোশামোদ করবে, মন যুগিয়ে চলবে। পাশাপাশি অমনি আমার মায়ের ছবি মনে আসে। মা কোন গুণে জ্যাঠাইমার চেয়ে কম? মাকে চা-বাগানে দেখেছি কল্যাণী মূর্তিতে–লোকজনকে খাওয়ানো-মাখানো, কুলীদের ছেলেমেয়েদের পুঁতির মালা কিনে দেওয়া, আদর-যত্ন করা, আমাদের একটু অসুখে রাত জেগে বিছানায় বসে থাকা।
কাছাকাছি কোন চা-বাগানের বাঙালীবাবু সোনাদায় নেমে যখন বাগানে যেত আমাদের বাসায় না খেয়ে যাবার উপায় ছিল না। আর সে-ই মা এখানে এঁদের সংসারের দাসী, পরনে ছেঁড়া ময়লা কাপড়, কাজ করতে পারলে সুখ্যাতি নেই, না পারলে বকুনি আছে, গালাগাল আছে–সবাই হেনস্থা করে, কারও কাছে এতটুকু মান নেই, মাথা তুলে বেড়াবার মুখ নেই। কেন, ঠাকুরকে ঘুষ দিতে পারেন না বলে? আমার মনে হ’ত জ্যাঠাইমাদের শালগ্রামশিলা এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে আছেন, তিনি ষোড়শোপচারে পুজো পেয়ে জ্যাঠাইমাকে বড় করে দিয়েছেন, অন্য সকলের উপর জ্যাঠাইমা যে অত্যাচার অবিচার করছেন, তা চেয়েও দেখছেন না ঠাকুর।
একদিন সন্ধ্যাবেলা ঠাকুরঘরে আরতি শুরু হয়েছে। নরু, সীতা, সেজ কাকার ছেলে পুলিন আর আমি দেখতে গেছি। পুরুতঠাকুর ওদের সবারই হাতে একটা ক’রে রূপোবাঁধানো চামর দিলে–আরতির সময় তারা চামর দুলুতে লাগল। আমার ও সীতার হাতে দিলে না। সীতা চাইতে গেল, তাও দিলে না। একটু পরে ধূপধুনোর ধোঁয়ায় ও সুগন্ধে দালান ভরে গিয়েছে, বুলু ও ফেণী কাঁসর বাজাচ্ছে, পুরুতঠাকুরের ছোট ভাই রাম ঘড়ি পিটচে, পুরুতঠাকুর তন্ময় হয়ে পঞ্চপ্রদীপে ঘিয়ের বাতি জ্বেলে আরতি করছে– আমি ও সীতা ছিটের দোলাইমোড়া ঠাকুরের আসনের দিকে চেয়ে আছি–এমন সময় আমার মনে হ’ল এ দালানে শুধু আমরা এই ক’জন উপস্থিত নেই, আরও অনেক লোক উপস্থিত আছে, তাদের দেখা যাচ্ছে না, তারা সবাই অদৃশ্য। আমার গা ঘুরতে লাগল, আর কানের পেছনে মাথার মধ্যে একটা জায়গায় যেন কতকগুলো পিঁপড়ে বাসা ভেঙে বেরিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে গেল। আমি জানি, এ আমার চেনা, জানা, বহুপরিচিত লক্ষণ, অদৃশ্য কিছু দেখবার আগেকার অবস্থা–চা-বাগানে এ-রকম কতবার হয়েছে। শরীরের মধ্যে কেমন একটা অস্বস্তি হয়–সে ঠিক বলে বোঝানো যায় না, জ্বর আসবার আগে যেমন লোক বুঝতে পারে এইবার জ্বর আসবে, এও ঠিক তেমনি। আমি সীতাকে কি বলতে গেলাম, পিছু হটে গিয়ে দালানের থামে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালাম, গা বমি-বমি করে উঠলে লোকে যেমন করে সে ভাবটা কাটাবার চেষ্টা করে, আমিও সেই রকম স্বাভাবিক অবস্থায় থাকবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগলাম–কিছুতেই কিছু হ’ল না, ধীরে ধীরে পূজার দালানের তিনবারের দেওয়াল আমার সামনে থেকে অনেক দূরে…অনেক দূরে সরে যেতে লাগল…কাঁসর ঘড়ির আওয়াজ ক্ষীণ হয়ে এল…কতকগুলো বেগুনি ও রাঙা রঙের আলোর চাকা যেন একটা আর একটার পিছনে তাড়া করছে…সারি সারি। বেগুনি ও রাঙা আলোর চাকার খুব লম্বা সারি আমার চোখের সামনে দিয়ে খেলে যাচ্ছে– তার পর আমার বাঁয়ে অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত একটা বড় নদী, ওপারেও সুন্দর গাছপালা, নীল আকাশ–এপারেও অনেক ঝোপ বন–কিন্তু যেন মনে হ’ল সব জিনিসটা আমি ঝাড়লণ্ঠনের তেকোণা কাচ দিয়ে দেখচি–নানা রঙের গাছপালা ও নদীর জলের ঢেউয়ের নানা রঙ–ওপারটায় লোকজনে ভরা, মেয়েও আছে, পুরুষও আছে-গাছপালার মধ্যে দিয়ে একটা মন্দিরের সরু চূড়া ঠেলে আকাশে উঠেছে..আর ফুল যে কত রঙের আর কত চমৎকার তা মুখে বলতে পারিনে, গাছের সারা গুঁড়ি ভ’রে যেন রঙিন ও উজ্জ্বল থোকা থোকা ফুল…হঠাৎ সেই নদীর একপাশে জলের ওপর ভাসমান অবস্থায় জ্যাঠামশায়ের ঠাকুর-ঘরটা একটু একটু ফুটে উঠল, তার চারিদিকে নদী, কড়িকাঠের কাছে কাছে সে নদীর ধারের ডাল তার থোকা থোকা ফুলসুদ্ধ হাওয়ায় দুলছে..ওদের সেই দেশটা যেন আমাদের ঠাকুরঘরের চারিপাশ ঘিরে..মধ্যে, ওপরে, নীচে, ডাইনে, বাঁয়ে আমার মন আনন্দে ভরে গেল…কান্না আসতে চাইল…কি জানি কোন ঠাকুরের ওপর ভক্তিতে–আমার ঘোর কাটল একটা চেঁচামেচির শব্দে। আমায় সবাই মিলে ঠেলচে। সীতা আমার ডান হাত জোর করে ধরে দাঁড়িয়ে আছে–পুরুতঠাকুর ও পুলিন রেগে আমায় কি বলচে– চেয়ে দেখি আমি ভোগের লুচির থালার অত্যন্ত কাছে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি–আমার কোঁচা লুটুচ্ছে উঁচু করে সাজানো ফুলকো লুচির ওপরে। তারপর যা ঘটল! পুরুতঠাকুর গালে চার-পাঁচটা চড় কষিয়ে দিলেন–মেজকাকা এসে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বললেন। জ্যাঠাইমা এসে নরু-পুলিনদের ওপর আগুন হয়ে বলতে লাগলেন, সবাই জানে আমি পাগল, আমার মাথার রোগ আছে, আমায় তারা কেন ঠাকুরদালানে নিয়ে গিয়েছিল আরতির সময়–
মেজকাকার মারের ভয়ে অন্ধকার রাত্রে জ্যাঠামশায়দের খিড়কীপুকুরের মাদার-তলায় একা এসে দাঁড়ালাম। সীতা গোলমালে টের পায় নি আমি কোথায় গিয়েছি। আমার গা কাঁপছিল ভয়ে–এ আমার কি হ’ল? আমার এমন হয় কেন? এ কি খুব শক্ত ব্যারাম? ঠাকুরের ভোগ আমি তো ইচ্ছে করে ছুঁই নি? তবে ওরা বুঝলে না কেন? এখন আমি কি করি?
আমি হিন্দু দেবদেবী জানতাম না, সে-শিক্ষা আজন্ম আমাদের কেউ দেয় নি। কিন্তু মিশনারী মেমদের কাছে জ্ঞান হওয়া পর্যন্ত যা শিখে এসেছি, সেই শিক্ষা অনুসারে অন্ধকারে মাদারগাছের গুঁড়ির কাছে মাটির ওপর হাঁটু গেড়ে হাতজোড় করে মনে মনে বললাম–হে প্রভু যীশু, হে সদাপ্রভু, তুমি জান আমি নির্দোষ–আমি ইচ্ছে করে করি নি কিছু, তুমি আমার এই রোগ সারিয়ে দাও, আমার যেন এ-রকম আর কখনও না হয়। তোমার জয় হোক, তোমার রাজত্ব আসুক, আমেন।
সকালে স্নান করে এসে দেখি সীতা আমাদের ঘরের বারান্দাতে এক কোণে খুঁটি হেলান দিয়ে বসে কি পড়ছে। আমি কাছে গিয়ে বললাম–দেখি কি পড়ছিস সীতা? সীতা এমন একমনে বই পড়ছে যে বই থেকে চোখ না তুলেই বললে–ও-পাড়ার বৌদিদির কাছ থেকে এনেছি–প্রফুল্লবালা-গোড়াটা একটু পড়ে দ্যাখো কেমন চমৎকার বই দাদা–
আমি বইখানা হাতে নিয়ে দেখলাম, নামটা প্রফুল্লবালা বটে। আমি বই পড়তে ভালবাসিনে, বইখানা ওর হাতে ফেরত দিয়ে বললাম–তুই এত বাজে বই পড়তে পারিস!
সীতা বললে–বাজে বই নয় দাদা, পড়ে দেখো এখন। জমিদারের ছেলে সতীশের সঙ্গে এক গরিব ভট্টাচার্যি বামুনের মেয়ে প্রফুল্লবালার দেখা হয়েছে। ওদের বোধ হয় বিয়ে হবে।
সীতা দেখতে ভাল বটে, কিন্তু যেমন সাধারণত ভাইয়েরা বোনেদের চেয়ে দেখতে ভাল হয়, আমাদের বেলাতেও তাই হয়েছে। আমাদের মধ্যে দাদা সকলের চেয়ে সুন্দর– যেমন রঙ, তেমনই চোখমুখ, তেমনই চুল–তারপর সীতা, তারপর আমি। দাদা যে সুন্দর, এ-কথা শত্রুতেও স্বীকার করে–সে আগে থেকে ভাল চোখ, ভাল মুখ, ভাল রঙ দখল করে বসেছে–আমার ও সীতার জন্যে বিশেষ কিছু রাখে নি। তা হলেও সীতা দেখতে ভাল। তা ছাড়া আবার শৌখীন–সর্বদা ঘষে মেজে, খোঁপাটি বেঁধে, টিপটি পরে বেড়ানো তার স্বভাব। কথা বলতে বলতে দশবার খোঁপায় হাত দিয়ে দেখছে খোঁপা ঠিক আছে কি-না, এ নিয়ে এ-বাড়িতে তাকে কম কথা সহ্য করতে হয় নি। কিন্তু সীতা বিশেষ কিছু গায়ে মাখে না, কারুর কথা গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না–চিরকালের একগুঁয়ে স্বভাব তার।
আমার মনে মাঝে মাঝে কষ্ট হয়, আমাদের তো পয়সা নেই, সীতাকে তেমন ভাল ঘরে বিয়ে দিতে পারব না–এই সব পাড়াগাঁয়ে আমার জ্যাঠামশায়দের মত বাড়িতে, আমার জ্যাঠাইমার মত শাশুড়ীর হাতে পড়বে–কি দুর্দশাটাই যে ওর হবে! ওর এত বই পড়ার ঝোঁক যে, এ-পাড়ার ও-পাড়ার বৌ-ঝিদের বাক্সে যত বই আছে চেয়ে-চিনতে এনে এ-সংসারের কঠিন কাজের ফাঁকে ফাঁকে সব পড়ে ফেলে দিয়েছে। জ্যাঠাইমা তো এমনিই বলেন, ও-সব অলুক্ষণে কাণ্ড বাপু–মেয়ে-মানুষের আবার অত বই পড়ার শখ, অত সাজগোজের ঘটা কেন? পড়বে তেমন শাশুড়ীর হাতে, ঝাঁটার আগায় বই পড়া ঘুচিয়ে দেবে তিন দিনে।
সীতার বুদ্ধি খুব। ‘শতগল্প’ বলে একখানা বই ও কোথা থেকে এনেছিল, তাতে ‘সোনামুখী ও ছাইমুখী’ বলে একটা গল্প আছে, সৎমার সংসারে গুণবতী লক্ষ্মীমেয়ে সোনামুখী ঝাঁটা লাথি খেয়ে মানুষ হ’ত–তারপর কোন দেশের রাজকুমারের সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে গেল ভগবানের দয়ায়–সীতা দেখি গল্পটার পাতা মুড়ে রেখেছে। ও-গল্পটার সঙ্গে ওর জীবনের মিল আছে, এই হয়ত ভেবেছে। কিন্তু সীতা একটি কথাও মুখ ফুটে বলে না কোন দিন। ভারি চাপা।
সীতা বই থেকে চোখ তুলে পথের দিকে চেয়ে বললে–ঐ হীরুঠাকুর আসচে দাদা, আমি পালাই–
আমি বললাম–বোস, হীরুঠাকুর কিছু বলবে না। ও ঠিক আজ এখানে খাবার কথা বলবে দ্যাখ।
হীরুঠাকুরকে এ-গাঁয়ে আসা পর্যন্ত দেখছি। রোগা কালো চেহারা, খোঁচা খোঁচা একমুখ কাঁচা-পাকা দাড়ি, পরনে থাকে আধময়লা থান, খালি পা, কাঁধে ময়লা চাদর, তার ওপরে একখানা ময়লা গামছা ফেলা। নিজের ঘরদোর নেই, লোকের বাড়ি বাড়ি খেয়ে বেড়ানো তার ব্যবসা। আমরা যখন এখানে নতুন এলাম, তখন কতদিন হীরুঠাকুর এসে আমাকে বলেছে, তোমার মাকে বল খোকা, আমি এখানে আজ দুটো খাবো। মাকে বলতেই তখুনি তিনি রাজী হতেন- মা চিরকাল এমন ছিলেন না, লোককে খাওয়াতে-মাখাতে চিরদিনই তিনি ভালবাসেন।
আমার কথাই ঠিক হ’ল। হারুঠাকুর এসে বললে- শোন খোকা, তোমার মাকে বলো আমি এখানে আজ দুপুরে চাট্টি ভাত খাবো। সীতা বই মুখে দিয়ে খিল খিল করে হেসেই খুন। আমি বললাম, হীরু-জ্যাঠা, আজকাল তো আমরা আলাদা খাইনে। জ্যাঠামশায়দের বাড়িতে খাই, বাবা মারা গিয়ে পর্যন্ত। আপনি সেজকাকাকে বলুন গিয়ে। সেজকাকা কাঁটালতলায় নাপিতের কাছে দাড়ি কামাচ্ছেন।
সেজকাকা লোক ভাল। হীরুঠাকুর আশ্বাস পেয়ে আমাদেরই ঘরের বারান্দায় বসল। সীতা উঠে একটা কম্বল পেতে দিলে। হীরুঠাকুর বললে, তোমার দাদা কোথায়? দাদার সঙ্গে ওর বড় ভাব। হীরুঠাকুরের গল্প দাদা শুনতে ভালবাসে, হীরুঠাকুরের কষ্ট দেখে দাদার দুঃখ খুব, হীরুঠাকুর না খেতে পেলে দাদা বাড়ি থেকে চাল চুরি করে দিয়ে আসে। এখানে যখন খেতে আসত তখুনি প্রথম দাদার সঙ্গে ওর আলাপ হয়, এই বারান্দায় বসেই। হীরুঠাকুরের কেউ নেই–একটা ছেলে ছিল, সে নাকি আজ অনেকদিন নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। হীরুঠাকুরের এখনও বিশ্বাস, ছেলে একদিন ফিরে আসবেই এবং অনেক টাকাকড়ি আনবে, তখন তার দুঃখ ঘুচবে। দাদা হীরুর ওই-সব গল্প মন দিয়ে বসে বসে শোনে। অমন শ্রোতা এ-গাঁয়ে বোধ হয় হীরুঠাকুর আর কখনও পায় নি।
খেতে বসে হীরুঠাকুর এক মহাগোলমাল বাধিয়ে বসল। জ্যাঠামশায়ের ছোট মেয়ে সরিকে ডেকে বললে, হীরু কারুর নাম মনে রাখতে পারে না, খুকী শোন, বাড়ির মধ্যে জিজ্ঞেস কর তো ডালের বাটিতে তাঁরা কি কিছু মিশিয়ে দিয়েছেন? আমার গা যেন ঘুরচে। সবাই জানে হীরুঠাকুরের মাথা খারাপ, সে ওরকম একবার আমাদের বাড়ি খেতে বসেও বলেছিল, কিন্তু বাড়িসুদ্ধ মেয়েরা বেজায় চটল এতে। চটবারই কথা। জ্যাঠাইমা বললেন–সেজঠাকুরপোর খেয়ে-দেয়ে তো আর কাজ নেই, ও আপদ মাসের মধ্যে দশদিন আসে এখানে খেতে। তার ওপর আবার বলে কি-না ডালে বিষ মিশিয়ে দিই আমরা। আ মরণ মুখপোড়া বামুন, তোকে বিষ খাইয়ে মেরে কি তোর লাকো টাকার তালুক হাত করব? আজ থেকে বলে দাও সেজঠাকুরপো, এ-বাড়ির দোর বন্ধ হয়ে গেল, কোনো দিন সদরের চৌকাঠ মাড়ালে ঝাঁটা মেরে তাড়াবো।
হীরু তখন খাওয়া শেষ করেছিল। জ্যাঠাইমার গালাগালি শুনে মুখখানা কাঁচুমাচু করে উঠে গেল। দাদা এ-সময় বাড়ি ছিল না।–আমাদের মুখে এর পর শুনে বললে–আহা, ও পাগল, ছেলের শোকে পাগল হয়েছে। ও কি বলে না-বলে তা কি ধরতে আছে? ছিঃ, খাবার সময় জ্যাঠাইমার গালমন্দ করা ভাল হয় নি। আহা!
সীতা বললে–গালাগাল দেওয়া ভাল হয় নি কেন, খুব ভাল হয়েছে। খামোকা বলবে যে বিষ মিশিয়ে দিয়েছে? লোকে কি মনে করবে?
দাদা আর কিছু বললে না, চুপ করে রইল। সে কারুর সঙ্গে তর্ক করতে পারে না, সীতার সঙ্গে তো নয়ই। একবার কেবল আমায় জিজ্ঞেস করলে–হীরুজ্যেঠা কোন দিকে গেল রে জিতু? আমি বললাম আমি জানিনে।
এর মাস দুই-তিন পরে, মাঘ মাসের শেষ, বিকেল বেলা। আমাদের ঘরের সামনে একটুখানি পড়ন্ত রোদে পিঠ দিয়ে স্কুলের অঙ্ক কষচি–এমন সময় দেখি হীরুঠাকুরকে সন্তর্পণে আস্তে আস্তে ধরে নিয়ে আসছে দাদা।
হীরুঠাকুরের চেহারা শীর্ণ, মাথার চুল আরও উসকোখুসকো, মুখ প্যাঙাস–জ্বরে যেমনি কাঁপছে, তেমনি কাশচে। শুনলাম আজ–কি চার পাঁচ দিন অসুখ অবস্থায়
আমাদেরই পাড়ায় ভট্টাচার্যিদের পুজোর দালানে শুয়ে ছিল। অসুখে কাশ-থুথু ফেলে ঘর অপরিষ্কার করে দেখে তারা এই অবস্থায় বলেছে সেখানে জায়গা হবে না। হীরুঠাকুর চলতে পারে না, যেমন দুর্বল, তেমনি জ্বর আর সে কি ভয়ানক কাশি! কোথায় যায়, তাই দাদা তাকে নিয়ে এসেছে জ্যাঠামশায়দের বাড়ি। ভয়ে আমার প্রাণ উড়ে গেল। দাদার কি এতটুকু বুদ্ধি দেননি ভগবান! এটা কি নিজেদের বাড়ি যে এখানে যা খুশি করা চলবে? কোন ভরসায় দাদা ওকে এখানে নিয়ে এল দ্যাখো তো?
যা ভয় করেছি, তাই হ’ল। হীরুকে অসুখ গায়ে হাত ধরে বাড়িতে এনেছে দাদা, এ কথা বিদ্যুতবেগে বাড়ির মধ্যে প্রচার হয়ে যেতেই আমার খুড়তুতো জাঠতুতো ভাইবোনরা সব মজা দেখতে বাইরের উঠোনে ছুটে এল, সেজকাকা এসে বললেন–না না–এখানে কে নিয়ে এল ওকে? এখানে জায়গা কোথায় যে রাখা হবে? কিন্তু ততক্ষণে জ্যাঠামশায়দের চণ্ডীমণ্ডপের দাওয়ায় হীরু ধুকছে, দাদা চণ্ডীমণ্ডপের পুরোনো সপটা তাকে পেতে দিয়েছে। তখনি একটা ও-অবস্থার রোগীকে কোথায় বা সরানো যায়? বাধ্য হয়ে তখনকার মত জায়গা দিতেই হ’ল।
কিন্তু এর জন্যে কি অপমানটাই সহ্য করতে হ’ল দাদাকে। এইজন্যেই বলচি দিনটা কখনো ভুলবো না। দাদাকে আমরা সবাই ভালবাসি, আমি সীতা দুজনেই। আমরা জানি সে বোকা, তার বুদ্ধি নেই, সে এখনও আমাদের চেয়েও ছেলেমানুষ, সংসারের ভালমন্দ সে কিছু বোঝে না, তাকে বাঁচিয়ে আড়াল করে বেরিয়ে আমরা চলি। দাদাকে কেউ একটু বকলে আমরা সহ্য করতে পারিনে, আর সেই দাদাকে বাড়ির মধ্যে ডেকে নিয়ে গিয়ে প্রথমে সেজকাকা আথালিপাতালি চড়চাপড় মারলেন। বললেন, বুড়ো ধাড়ী কোথাকার, ওই হাঁপকাশের রুগী বাড়ি নিয়ে এলে তুমি কার হুকুমে? তোমার বাবার বাড়ি এটা? এতটুকু জ্ঞান হয় নি তোমার? সাহসও তো বলিহারি, জিজ্ঞেস না বাদ না কাউকে, একটা কঠিন রুগী বাড়ি নিয়ে এসে তুললে কোন সাহসে? নবাব হয়েছ না ধিঙ্গী হয়েছ? না তোমার চা-বাগান পেয়েছ?
এর চেয়ে বেশী কষ্ট হ’ল যখন জ্যাঠাইমা অনেক গালিগালাজের পর রোয়াকে দাঁড়িয়ে হুকুম জারি করলেন, যাও, রুগী ছুঁয়ে ঘরের দোরে উঠতে পাবে না, পুকুর থেকে গায়ের ও-কোটসুদ্ধ ডুব দিয়ে এস গিয়ে।
মাঘ মাসের শীতের সন্ধ্যা আর সেই কনকনে ঠাণ্ডা পুকুরের জল–তার ওপর চা বাগানের আমলের ওই ছেঁড়া গরম কোটটা ছাড়া দাদার গায়ে দেবার আর কিছু নেই, দাদা গায়ে দেবে কি নেয়ে উঠে? সীতা ছুটে গিয়ে শুকনো কাপড় নিয়ে এসে পুকুরের ধারে দাঁড়িয়ে রইল। মাও এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিনি ভালমানুষ, দাদাকে একটা কথাও বললেন না, কেবল ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে জল থেকে সে যখন উঠে এল তখন নিজের হাতে গামছা দিয়ে তার মাথা মুছিয়ে দিলেন, সীতা শুকনো কাপড় এগিয়ে দিলে, আমি গায়ের কোটটা খুলে পরতে দিলাম। রাত্রে মা সাবু করে দিলেন আমাদের ঘরের উনুনে–দাদা গিয়ে হীরুঠাকুরকে খাইয়ে এল।
সকালবেলা সেজকাকা ও জ্যাঠামশাই দত্তদের কাঁটালবাগানের ধারে পোড়ো জমিতে বাড়ির কৃষাণকে দিয়ে খেজুরপাতার একটা কুঁড়ে বাঁধালেন এবং লোকজন ডাকিয়ে হীরুকে ধরাধরি করে সেখানে নিয়ে গেলেন। দাদা চুপিচুপি একবাটি সাবু মা’র কাছ থেকে করে নিয়ে দিয়ে এল। দিন-দুই এই অবস্থায় কাটলো। মুখুজ্জে-বাড়ির বড়মেয়ে নলিনীদি রাত্রে একবাটি বার্লি দিয়ে আসতো আর সকালবেলা যাবার সময় বাটিটা ফিরিয়ে নিতে যেত।
একদিন রাতে দাদা বললে–চল জিতু, আজ হীরুজ্যাঠার ওখানে রাতে থাকবি? রামগতি-কাকা দেখে বলেছে অবস্থা খারাপ। চল আগুন জ্বালাবো এখন, বড্ড শীত নইলে।
রাত দশটার পর আমি ও দাদা দুজনে গেলাম। আমরা যাওয়ার পর নলিনীদি সাবু নিয়ে এল। বললে, কি রকম আছে রে হীরুকাকা? তারপর সে চলে গেল। নারকোলের মালা দু’তিনটে শিয়রের কাছে পাতা, তাতে কাশ থুথু ফেলেচে রুগী। আমার গা কেমন বমি-বমি করতে লাগল। আর কি কনকনে ঠাণ্ডা! খেজুরের পাতার ঝাঁপে কি মাঘ মাসের শীত আটকায়? দত্তদের কাঁটালবাগান থেকে শুকনো কাঁটালপাতা নিয়ে এসে দাদা আগুন জ্বাললে। একটু পরে দুজনেই ঘুমিয়ে পড়লাম। কত রাত্রে জানি না, আমার মনে হ’ল হীরুজ্যাঠা আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। হীরুজ্যাঠা আর কাশচে না, তার রোগ যেন সেরে গিয়েছে! আমার দিকে চেয়ে হেসে বললে, জিতু, আমি বাঁশবেড়ে যাচ্ছি গঙ্গা নাইতে। আমায় বড় কষ্ট দিয়েছে হরিবল্লভ আমার জ্যাঠামশাই, আমি বলে যাচ্ছি, নির্বংশ হবে নির্বংশ হবে। তোমরা বাড়ি গিয়ে শোও গে যাও।
আমার গা শিউরে উঠলো–এত স্পষ্ট কথাগুলো কানে গেল, এত স্পষ্ট হীরুজ্যাঠাকে দেখলাম যে বুঝে উঠতে পারলাম না প্রত্যক্ষ দেখছি, না স্বপ্ন দেখছি। ঘুম কিন্তু ভেঙে গিয়েছিল, দাদা দেখি তখনও কুঁকড়ি হয়ে শীতে ঘুমুচ্ছে, কাঁটালপাতার আগুন নিভে জল হয়ে গিয়েছে, হীরুজ্যাঠাও ঘুমুচ্ছে মনে হ’ল। বাইরে দেখি ভোর হয়ে গিয়েছে।
দাদাকে উঠিয়ে নলিনীদিদির বাবা রামগতি মুখুজ্জেকে ডাকিয়ে আনলাম। তিনি এসে দেখেই বললেন, ও তো শেষ হয়ে গিয়েছে। কতক্ষণ হ’ল? তোরা কি রাত্রে ছিলি নাকি এখানে?
হীরুঠাকুরের মৃত্যুতে চোখের জল এক দাদা ছাড়া বোধ হয় আর কেউ ফেলে নি।
অনেকদিন পরে শুনেছিলাম, হীরুঠাকুর পৈতৃক কি জমিজমা ও দুখানা আম-কাঁটালের বাগান বন্ধক রেখে জ্যাঠামশায়ের কাছে কিছু টাকা ধার করে এবং শেষ পর্যন্ত হীরুঠাকুর সে টাকা শোধ না করার দরুন জ্যাঠামশায় নালিশ করে নিলামে সব বন্ধকী বিষয় নিজেই কিনে রাখেন। এর পর হীরুঠাকুর আপসে কিছু টাকা দিয়ে সম্পত্তিটা ফিরিয়ে নিতে চেয়েছিল–জ্যাঠামশায় রাজী হন নি। কেবল বলেছিলেন ব্রাহ্মণের ভিটে আমি চাইনে– ওটা তোমায় ফিরিয়ে দিলাম। হীরু তা নেয় নি, বলেছিল, সব যে পথে গিয়েছে, ও ভিটেও সে পথে যাক। এর কিছুকাল পরেই তার মাথা খারাপ হয়ে যায়।
বিষয় বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে জ্যাঠামশায়ের দান-ধ্যান ধর্মানুষ্ঠান বেড়ে চলেছিল। প্রতি পূর্ণিমায় তাঁদের ঘরে সত্যনারায়ণের পূজা হয় যে তা নয় শুধু–একটি গরিব ছাত্রকে জ্যাঠাইমা বছরে একটি টাকা দিতেন বই কেনবার জন্যে, শ্রাবণ মাসে তাঁদের আবাদ থেকে নৌকা আসে নানা জিনিসপত্র বোঝাই হয়ে–বছরের ধান, জালাভরা কইমাছ, বাজরাভরা হাঁসের ডিম, তিল, আকের গুড় আরও অনেক জিনিস। প্রতি বছরই সেই নৌকায় দুটি একটি হরিণ আসে। ধনধান্যপূর্ণ ডিঙা নিরাপদে দেশে পৌঁচেছে এবং তার জিনিসপত্র নির্বিঘ্নে ভাঁড়ার-ঘরে উঠল এই আনন্দে তাঁরা প্রতিবার শ্রাবণ মাসে পাঁটা বলি দিয়ে মনসাপূজা করতেন ও গ্রামের ব্রাহ্মণ খাওয়াতেন। বৈশাখ মাসে গৃহদেবতা। গোপীনাথ জীউর পুজোর পালা পড়ল ওঁদের। জ্যাঠামশায় গরদের জোড় প’রে লোকজন ও ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নিয়ে কাঁসরঘণ্টা, ঢাকঢোল বাজিয়ে ঠাকুর নিয়ে এলেন ও-পাড়ার জ্ঞাতিদের বাড়ি থেকে–জ্যাঠাইমা খুড়ীমারা বাড়ির দোরে দাঁড়িয়ে ছিলেন–প্রকাণ্ড পেতলের সিংহাসনে বসানো শালগ্রাম বয়ে আনছিলেন জ্যাঠামশায় নিজে–তিনি বাড়ি ঢুকবার সময়ে জ্যাঠাইমা জলের ঝারা দিতে দিতে ঠাকুর অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেলেন। মেয়েরা শাঁক বাজাতে লাগলেন, উলু দিলেন। আমি, সীতা ও দাদা আমাদের ঘরের বারান্দা থেকে দেখছিলাম-অত্যন্ত কৌতূহল হলেও কাছে যেতে সাহস হ’ল না। মাকে মেমে পড়াত সে-কথা ওঁদের কানে যাওয়া থেকে মানুষের ধারা থেকে আমরা নেমে গিয়েছি ওঁদের চোখে–আমরা খৃস্টান, আমরা নাস্তিক, পাহাড়ী জানোয়ার–ঘরদোরে ঢুকবার যোগ্য নই। বৈশাখ মাসের প্রতিদিন কত কি খাবার তৈরি হতে লাগল ঠাকুরের ভোগের জন্যে–ওঁরা পাড়ার ব্রাহ্মণদের নিমন্ত্রণ করে প্রায়ই খাওয়াতেন, রাত্রে শীতলের লুচি ও ফল-মিষ্টান্ন পাড়ার ছেলেমেয়েদের ডেকে দিতে দেখেছি তবুও সীতার হাতে একখানা চন্দ্রপুলি ভেঙে আধখানিও কোন দিন দেন নি।
জ্যাঠাইমা এ সংসারের কর্ত্তী, কারণ জ্যাঠামশাই রোজগার করেন বেশি। ফর্সা মোটাসোটা এক-গা গহনা, অলঙ্কারে পরিপূর্ণ–এই হলেন জ্যাঠাইমা। এ-বাড়িতে নববধূরূপে তিনি আসবার পর থেকেই সংসারের অবস্থা ফিরে যায়, তার আগে এঁদের অবস্থা খুব ভাল ছিল না–তাই তিনি নিজেকে ভাবেন ভাগ্যবতী। এ-বাড়িতে তাঁর উপর কথা বলবার ক্ষমতা নেই কারও। তাঁর বিনা হুকুমে কোন কাজ হয় না। এই জ্যৈষ্ঠ মাসে এত আম বাড়িতে, বৌদের নিয়ে খাবার ক্ষমতা নেই, যখন বলবেন খাও গে, তখন খেতে পাবে। জ্যাঠামশায়ের বড় ও মেজ ছেলে, শীতলদা ও সলিলদার বিয়ে হয়েছে, যদিও তাদের বয়েস খুব বেশী নয় এবং তাদের বৌয়েদের বয়েস আরও কম–দুই ছেলের এই দুই বৌ, ও বাড়িতে গলগ্রহ হয়ে আছে এক ভাগ্নেবৌ তার ছেলেমেয়ে নিয়ে, আর আমার মা আমাদের নিয়ে-–এ ছাড়া ভুবনের মা আছে, কাকীমারা আছেন–এর মধ্যে এক ছোট কাকীমা বাদে আর সব জ্যাঠাইমার সেবাদাসী। ছোট কাকীমা বাদে এইজন্যে যে তিনি বড়মানুষের মেয়ে–তাঁর উপর জ্যাঠাইমার প্রভুত্ব বেশি খাটে না।
প্রতিদিন খাওয়ার সময় কি নির্লজ্জ কাণ্ডটাই হয়! রোজ রোজ দেখে সয়ে গিয়েছে যদিও, তবুও এখনও চোখে কেমন ঠেকে। রান্নাঘরে একসঙ্গে ভাগ্নে, জামাই, ছেলেরা খেতে বসে। ছেলেদের পাতে, জামাইয়ের পাতে বড় বড় জামবাটিতে ঘন দুধ, ভাগ্নেদের পাতে হাতা করে দুধ। মেয়েদের খাবার সময় সীতা, ভাগ্নেবৌ এরা সবাই কলায়ের ডাল মেখে ভাত খেয়ে উঠে গেল–নিজেদের দল, দুই বৌ, মেয়ে নলিনীদি, নিজের জন্যে বাটিতে বাটিতে দুধ আম বাতাসা। নলিনীদি আবার মধু দিয়ে আম দুধ খেতে ভালবাসে–মধুর অভাব নেই, জ্যাঠামশাই প্রতি বৎসর আবাদ থেকে ছোট জালার একজালা মধু নিয়ে আসেন–নলিনীদি দুধ দিয়ে ভাত মেখেই বলবে, মা আমায় একটু মধু দিতে বল না সদুর মাকে। কালেভদ্রে হয়ত জ্যাঠাইমার দয়া হ’ল–তিনি সীতার পাতে দুটো আম দিতে বললেন কি এক হাতা দুধ দিতে বললেন–নয়তো ওরা এই কলায়ের ডাল মেখে খেয়েই উঠে গেল। সীতা সে-রকম মেয়ে নয় যে মুখ ফুটে কোন দিন কিছু বলবে, কিন্তু সেও তো ছেলেমানুষ, তারও তো খাবার ইচ্ছে হয়? আমি এই কথা বলি, যদি খাবার জিনিসের বেলায় কাউকে দেবে, কাউকে বঞ্চিত করবে, তবে একসঙ্গে সকলকে খেতে না বসালেই তো সব চেয়ে ভাল?
একদিন কেবল সীতা বলেছিল আমার কাছে–দাদা, জ্যাঠাইমারা কি রকম লোক বল দিকি? মা তাল তাল বাটনা বাটবে, বাসন মাজবে, রাজ্যির বাসি কাপড় কাচবে, কিন্তু এত ডাবের ছড়াছড়ি এ বাড়িতে, গাছেরই তো ডাব, একাদশীর পরদিন মাকে কোনো দিন বলেও না যে একটা ডাব নিয়ে খাও।
আমি মুখে মুখে বানিয়ে কথা বলতে ভালবাসি। আপন মনে কখনও বাড়ির কর্তার মত কথা বলি, কখনও চাকরের মত কথা বলি। সীতাকে কত শুনিয়েছি, একদিন মাকেও শুনিয়েছিলাম। একদিন ও-পাড়ার মুখুজ্জেবাড়িতে বীরুর মা, কাকীমা, দিদি এরা সব ধরে পড়ল আমাকে বানিয়ে বানিয়ে কিছু বলতে হবে।
ওদের রান্নাবাড়ির উঠোনে, মেয়েরা সব রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খানিকটা ভাবলাম কি বলব? সেখানে একটা বাঁশের ঘেরা পাঁচিলের গায়ে ঠেসানো ছিল। সেইটের দিকে চেয়ে আমার মাথায় বুদ্ধি এসে গেল। এই বাঁশের ঘেরাটা হবে যেন আমার স্ত্রী, আমি যেন চাকরি করে বাড়ি আসছি, হাতে অনেক জিনিসপত্র। ঘরে যেন সবে ঢুকেছি, এমন ভাব করে বললাম–ওগো কই, কোথায় গেলে, ফুলকপিগুলো নামিয়ে নাও না? ছেলেটার জ্বর আজ কেমন আছে? মেয়েরা সব হেসে এ ওর গায়ে গড়িয়ে পড়ল।
আমার উৎসাহ গেল আরও বেড়ে। আমি বিরক্তির সুরে বললাম, আঃ, ঐ তো তোমার দোষ! কুইনিন দেওয়া আজ খুব উচিত ছিল। তোমার দোষেই ওর অসুখ যাচ্ছে না। খেতে দিয়েছ কি?
আমার স্ত্রী অপ্রতিভ হয়ে খুব নরম সুরে কি একটা জবাব দিতেই রাগ পড়ে গেল আমার। বললাম–ওই পুঁটলিটা খোলো, তোমার একজোড়া কাপড় আছে আর একটা তরল আলতা–মেয়েরা আবর খিল খিল করে হেসে উঠল।
বীরুর ছোট বৌদিদি মুখে কাপড় খুঁজে হাসতে লাগলো। আমি বললাম–ইয়ে করো, আগে হাত-পা ধোয়ার জল দিয়ে একটু চায়ের জল চড়াও দিকি? সেই কখন ট্রেনে উঠেচি–ঝাঁকুনির চোটে আর এই দু-কোশ হেঁটে খিদে পেয়ে গিয়েছে–আর সেই সঙ্গে একটু হালুয়া–কাগজের ঠোঙা খুলে দেখ কিশমিশ এনেচি কিনে, বেশ ভাল কাবুলী-_
বীরুর কাকীমা তো ডাক ছেড়ে হেসে উঠলেন। বীরুর মা বললেন–ছোঁড়া পাগল! কেমন সব বলচে দেখ, মাগো মা, উঃ–আর হেসে পারিনে!
বীরুর ছোট বৌদিদির দম বন্ধ হয়ে যাবে বোধ হয় হাসতে হাসতে। বললে–ওঃ মা, আমি যাব কোথায়! ওর মনে মনে ওই সব শখ আছে, ওর ইচ্ছে ওর বিয়ে হয়, বৌ নিয়ে অমনি সংসার করে–উঃ মা রে!
সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। আমি রান্নাঘরে বসে স্ত্রীর সঙ্গে গল্প করচি। রান্না এখনও শেষ হয়নি। আমি বললাম–চিংড়ি মাছটা কেমন দেখলে, খুব পচেনি তো? কালিয়াটায় ঝাল একটু বেশি করে দিও।
বীরুর কাকীমা বললেন, হাঁ রে তুই কি কেবল খাওয়া-দাওয়ার কথা বলবি বৌয়ের সঙ্গে? কিন্তু আর কি ধরনের কথা বলব খুঁজে পাইনে। ভাবলাম খানিকক্ষণ, আর কি কথা বলা উচিত? আমি এই ধরনের কথা সকলকে বলতে শুনেচি স্ত্রীর কাছে। ভেবে ভেবে বললাম-খুকীর জন্যে জামাটা আনবো, কাল ওর গায়ের মাপ দিও তো। আর জিজ্ঞেস করো কি রঙ ওর পছন্দ–না, না–এখন আর ঘুম ভাঙিয়ে জিজ্ঞেস করবার দরকার নেই, ছেলেমানুষ ঘুমুচ্ছে, থাক। কাল সকালেই– খুব গম্ভীর মুখে এ-কথা বলতেই মেয়েরা আবার হেসে উঠল দেখে আমি ভারি খুশি হয়ে উঠলাম। আরও বাহাদুরি নেবার ইচ্ছায় উৎসাহের সুরে বললাম- আমি নেপালী নাচ জানি–চা-বাগানে থাকতে আমি দেখে দেখে শিখেছি।
মেয়েরা সবাই বলে উঠলো, তাও জানিস নাকি? বা রে! তা তো তুই বলিস নি কোনোদিন? দেখি–দেখি—
কিন্তু আর একজন লোক দরকার যে? আমার সঙ্গে আর কে আসবে? সীতা থাকলে ভাল হত। সেও জানে। আপনাদের বীণা কোথায় গেল? সে হলেও হয়।
এ কথায় মেয়েরা কেন যে এত হেসে উঠল হঠাৎ, তা আমি বুঝতে পারলাম না। বীণা বীরুর মেজ বোন, আমার চেয়ে কিছু ছোট, দেখতে বেশ ভাল। সে ওখানে ছিল না। তখন–একা একা নেপালী নাচ হয় না বলে বেশী বাহাদুরিটা আমার আর নেওয়া হয় নি সে-দিন।
সীতার বই পড়ার ব্যাপার নিয়ে জ্যাঠাইমা সকল সময় সীতাকে মুখনাড়া দেন। সীতা যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ফিটফাট থাকতে ভালবাসে এটাও জ্যাঠাইমা বা কাকীমারা দেখতে পারেন না। সীতা চিরকাল ওই রকম থেকে এসেছে চা-বাগানে। একটিমাত্র মেয়ে, মা তাকে সব সময় সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখতে ভালবাসতেন, কতকটা আবার গড়ে উঠেছিল মিস নর্টনের দরুন। মিস নর্টন মাকে পড়াতে এসে নিজের হাতে সীতার চুল আঁচড়ে দিত, চুলে লাল ফিতে বেঁধে দিত, হাত ও মুখ পরিষ্কার রাখতে শেখাত। এখানে এসে সীতার দুখানার বেশি তিনখানা কাপড় জোটেনি কোন সময়–জামা তো নেই-ই। জ্যাঠাইমা বলেন, মেয়েমানুষের আবার জামা গায়ে কিসের? কিন্তু ওরই মধ্যে সীতা ফরসা কাপড়খানি পরে থাকে, চুলটি টান টান করে বেঁধে পেছনে গোল খোঁপা বেঁধে বেড়ায়, কপালে টিপ পরে–এ-গাঁয়ের এক পাল অসভ্য অপরিষ্কার ছেলেমেয়ের মধ্যে ওকে সম্পূর্ণ অন্য রকমের দেখায়, যে-কেউ দেখলেই বলতে পারে ও এ-গাঁয়ের নয়, এ অঞ্চলের না–ও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।
দুটো জিনিস সীতা খুব ভালবাসে ছেলেবেলা থেকে–সাবান আর বই। আর এখানে এসে পর্যন্ত ঠিক ওই দুটো জিনিসই মেলে না–এ-বাড়িতে সাবান কেউ ব্যবহার করে না, কাকীমাদের বাক্সে সাবান হয়ত আছে কিন্তু সে বাক্স-সাজানো হিসাবে আছে, যেমন তাঁদের বাক্সে কাঁচের পুতুল আছে, চীনেমাটির হরিণ, খোকা পুতুল, উট আছে–তেমনি। তবুও সাবান বরং খুঁজলে মেলে বাড়িতে–কেউ ব্যবহার করুক আর নাই করুক–বই খুঁজলেও মেলে না–দুখানা বই ছাড়া–নতুন পাঁজি আর সত্যনারায়ণের পুঁথি। আমরা তো চা-বাগানে থাকতাম, সে তো বাংলা দেশেই নয়–তবুও আমাদের বাক্সে অনেক বাংলা বই ছিল। নানা রকমের ছবিওয়ালা বাংলা বই–যীশুর গল্প, পরিত্রাণের কথা, জবের গল্প, সুবৰ্ণবণিক পুত্রের কাহিনী আরও কত কি। এর মধ্যে মিশনারি মেমেরা অনেক দিয়েছিল, আবার বাবাও কলকাতা থেকে ডাকে আনাতেন–সীতার জন্যে এনে দিয়েছিলেন। কঙ্কাবতী, হাতেম তাই, হিতোপদেশের গল্প, আমার জন্যে একখানা ‘ভূগোল-পরিচয়’ বলে বই আর একখানা ‘ঠাকুরদার ঝুলি’। আমি গল্পের বই পড়তে তত ভালবাসিনে, দু-তিনটে গল্প পড়ে আমার বইখানা আমি সীতাকে দিয়ে দিয়েছিলাম।
আমার ভাল লাগে যীশুখৃষ্ট্রের কথা পড়তে। পর্বতে যীশুর উপদেশ, যীশুর পুনরুত্থান, অপব্যয়ী পুত্রের প্রত্যাবর্তন। এ সব আমার বেশ লাগে। এখানে ও সব বই পাওয়া যায় না বলে পড়িনে। যীশুর কথা এখানে কেউ বলেও না। একখানা খৃস্টের রঙীন ছবি আমার কাছে আছে–মিস নর্টন দিয়েছিল–সেখানা আমার বড় প্রিয়। মাঝে মাঝে বার ক’রে দেখি।
হিন্দু দেবতার কোন মূর্তি আমি দেখিনি, জ্যাঠামশায়ের বাড়িতে যা পুজো করেন, তা গোলমত পাথরের নুড়ি। এ-গ্রামে দুর্গাপূজা হয় না, ছবিতে দুর্গামূর্তি দেখেছি, ভাল বুঝতে পারিনে, কিন্তু একটা ব্যাপার হয়েছে মধ্যে। চৌধুরীপাড়ায় বড় পুকুরের ধারের পাকুড়গাছের তলায় কালো পাথরের একটা দেবমূর্তি গাছের গুঁড়িতে ঠেসানো আছে–আমি একদিন দুপুরে পাকুড়তলা দিয়ে যাচ্ছি, বাবা তখন বেঁচে আছেন কিন্তু তাঁর খুব অসুখ– ওই সময় মূর্তিটা আমি প্রথম দেখি–জায়গাটা নির্জন, পাকুড়গাছের ডালপালার পিছনে অনেকখানি নীল আকাশ, মেঘের একটা পাহাড় দেখাচ্ছে ঠিক যেন বরফে মোড়া কাঞ্চনজঙ্ঘা–একটা হাত ভাঙা যদিও কিন্তু কি সুন্দর যে মুখ মূর্তিটার, কি অপূর্ব গড়ন–আমার হঠাৎ মনে হ’ল ওই পাথরের মূর্তির পবিত্র মুখের সঙ্গে ক্রুশবিদ্ধ যীশুখৃষ্ট্রের মুখের মিল আছে–কেউ ছিল না তাই দেখেনি–আমার চোখে জল এল, আমি একদৃষ্টিতে মূর্তিটার মুখের দিকে চেয়েই আছি–ভাবলাম জ্যাঠামশায়রা পাথরের নুড়ি পুজো করে কেন, এমন সুন্দর মূর্তির দেবতা কেন নিয়ে গিয়ে পুজো করে না? তার পরে শুনেচি ঐ দীঘি খুঁড়বার সময়ে আজ প্রায় পঁচিশ বছর আগে মূর্তিটা হাতভাঙা অবস্থাতেই মাটির তলায় পাওয়া যায়। সীতাকে নিয়ে গিয়ে দেখিয়েছিলাম একবার––একবার সীতা জবা, আকন্দ, ঝুমকো ফুলের একছড়া মালা গেঁথে মূর্তির গলায় পরিয়ে দিয়েছিল। অমন সুন্দর দেবতাকে আজ পঁচিশ বছর অনাদরে গ্রামের বাইরের পুকুরপাড়ে অমন করে কেন যে ফেলে দিয়েছে এরা।
একবার একখানা বই পড়লাম–বইখানার নাম চৈতন্যচরিতামৃত। এক জায়গায় একটি কথা পড়ে আমার ভারি আনন্দ হ’ল। চৈতন্যদেব ছেলেবেলায় একবার আঁস্তাকুড়ে এঁটো হাঁড়িকুড়ি যেখানে ফেলে, সেখানে গিয়েছিলেন বলে তাঁর মা শচীদেবী খুব বকেন। চৈতন্যদেব বললেন–মা পৃথিবীর সর্বত্রই ঈশ্বর আছেন, এই আঁস্তাকুড়েও আছেন। ঈশ্বর যেখানে আছেন, সে-জায়গা অপবিত্র হবে কি করে?
ভাবলাম জ্যাঠাইমার বিরুদ্ধে চমৎকার যুক্তি পেয়েছি ওঁদের ধর্মের বইয়ে, চৈতন্যদেব অবতার, তাঁরই মুখে। জ্যাঠাইমাকে একদিন বললাম কথাটা। বললাম–জ্যাঠাইমা, আপনি যে বাড়ির পিছনে বাঁশবনে গেলে কি শেওড়া গাছে কাপড় ঠেকলে হাত-পা না ধুয়ে, কাপড় না ছেড়ে ঘরে ঢুকতে দেন না, চৈতন্যচরিতামৃতে কি লিখেছে জানেন?
চৈতন্যদেবের সে কথাটা বলবার সময়ে আনন্দে মন আমার ভ’রে উঠল–এমন নতুন কথা, এত সুন্দর কথা আমি কখনও শুনিনি। ভাবলাম জ্যাঠাইমা বই পড়েন না বলে এত সুন্দর কথা যে ওঁদের ধর্মের বইয়ে আছে তা জানেন না–আমার মুখে শুনে জেনে নিশ্চয়ই নিজের ভুল বুঝে খুব অপ্রতিভ হয়ে যাবেন।
জ্যাঠাইমা বললেন–তোমাকে আর আমায় শাস্তর শেখাতে হবে না। তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেচে, উনি এসেচেন আজ আমায় শাস্তর শেখাতে! হিঁদুর আচার-ব্যবহার তোরা জানবি কোত্থেকে রে ডেঁপো ছোঁড়া। তুই তো তুই, তোর মা বড় জানে, তোর বাবা বড় জানতো–
আমি অবাক হয়ে গেলাম। জ্যাঠাইমা এমন সুন্দর কথা শুনে চটলেন কেন? তা ছাড়া আমি নিজে কিছু বলেছি কি?
আগ্রহের সুরে বললাম–আমার কথা নয় জ্যাঠাইমা, চৈতন্যদেব বলেছিলেন তাঁর মা শচীদেবীকে–চৈতন্যচরিতামৃতে লেখা আছে–দেখাবো বইখানা?
–খুব তক্কোবাজ হয়েচ? থাক, আর বই দেখাতে হবে না। তোমার কাছে আমি গুরুমন্তর নিতে যাচ্ছিনে–এখন যাও আমার সামনে থেকে, আমার কাজ আছে–তোমার তক্কো শুনবার সময় নেই।
বা রে, তর্কবাজির কি হ’ল এতে? মনে কষ্ট হ’ল আমার। সেই থেকে জ্যাঠাইমাকে আর কোন কথা বলিনি।
সীতা ইতিমধ্যে এক কাণ্ড করে বসল। জ্যাঠামশাইদের বাড়ির পাশে যদু অধিকারীর বাড়ি। তারা বারেন্দ্ৰশ্রেণীর ব্রাহ্মণ। তাদের বাড়িতে যদু অধিকারীর বড় মেয়েকে বিয়ের জন্য দেখতে এল চার-পাঁচজন ভদ্রলোক কলকাতা থেকে। সীতা সে-সময় সেখানে উপস্থিত ছিল।
যদু অধিকারীর বাড়ির মেয়েরা তাকে নাকি জিজ্ঞেস করেছে–শোন সীতা, আচ্ছা উমার যদি বিয়ে না হয় ওখানে, তোর বিয়ে দিয়ে যদি দিই, তোর পছন্দ হয় কাকে বল তো?
সীতা বুঝতে পারেনি যে তাকে নিয়ে ঠাট্টা করচে–বলেচে নাকি চোখে-চশমা কে একজন এসেছিল তাকে।
ওরা সে কথা নিয়ে হাসাহাসি করচে। জ্যাঠাইমার কানেও গিয়েছে কথাটা। জ্যাঠাইমা ও সেজকাকীমা মিলে সীতাকে বেহায়া, বোকা, বদমাইশ জ্যাঠা মেয়ে, যা তা বলে গালাগালি আরম্ভ করলেন। আরও এমন কথা সব বললেন যা ওঁদের মুখ দিয়ে বেরুলো কি করে আমি বুঝতে পারিনি। আমি সীতাকে বকলাম, মাও বকলেন–তুই যাস কেন যেখানে সেখানে, আর না বুঝে যা তা বলিসই বা কেন? এ-সব জায়গার ধরন তুই কি বুঝিস?
সীতার চোখ ছল ছল ক’রে উঠল। সে অতশত বোঝেনি, কে জানে ওরা আবার এখানে বলে দেবে! সে মনে যা এসেছে, মুখে সত্যি কথাই বলেচে। এ নিয়ে এত কথা উঠবে তা বুঝতেই পারেনি।