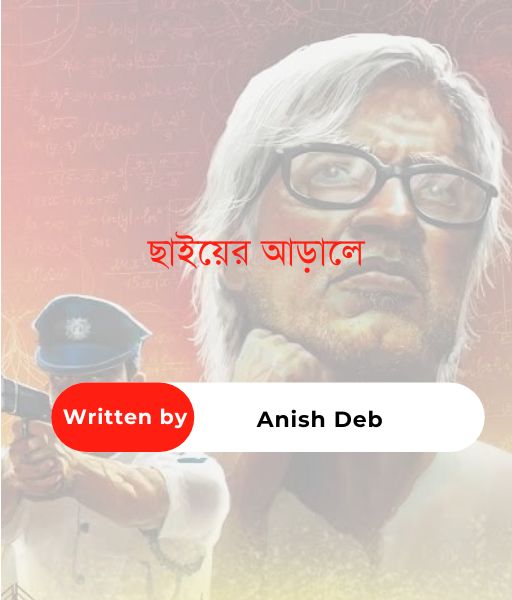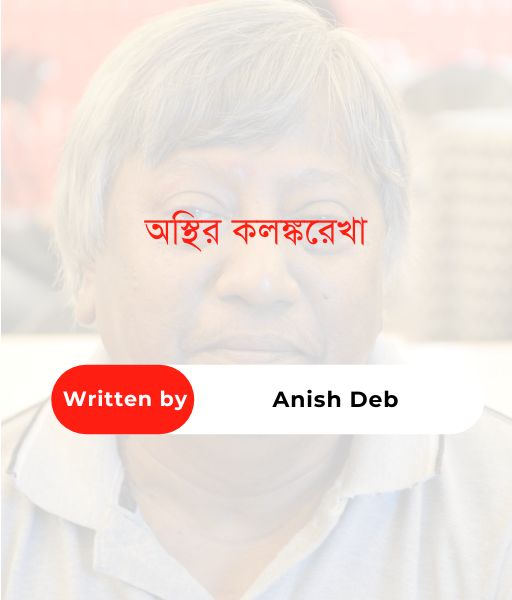হারিয়ে যাওয়ার ভয়
সপ্তাহ দুয়েক আগে কলেজ স্ট্রিট অঞ্চলের একটি ছোট রেস্তোরাঁয় বহু পুরোনো একটা সস্তা ডায়েরি পাওয়া যায়। রেস্তোরাঁর মালিক দিব্যি কেটে বলেছেন, এই নোটবইটা হঠাৎই তাঁর নজরে পড়ার আগে প্রায় ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে কোনও লোক তার দোকানে আসেনি। ডায়েরির লেখাগুলো ভারী অদ্ভুত। কেন অদ্ভুত সেটা মনে হয় পড়লেই বোঝা যাবে।
শনিবার। সকাল।
জানি, এগুলো লিখে রাখা মোটেই ঠিক হচ্ছে না। রীণা যদি একবার দেখতে পায়, তা হলে কী হবে, সেটা সহজেই আইডিয়া করতে পারছি। আমাদের দশ বছরের বিয়েটা উচ্ছের মতো তেতো হয়ে উচ্ছন্নে চলে যাবে।
কিন্তু না লিখেও যে পারছি না! এই লেখা-লেখা অভ্যেসটা যেন একটা ম্যানিয়ার মতো আমার রক্তে মিশে আছে। যতক্ষণ না সাদা-কালো লেখায় মনের কথাটা লিখতে পারছি, ততক্ষণ শাস্তি নেই। মন হালকা করতে গেলে এই লেখালেখিটা জরুরি। কিন্তু মনকে জটিল করা যত সহজ, হালকা করা বুঝি ততটাই কঠিন।
সুতরাং এখন ফিরে যেতে হবে মাসকয়েক আগে।
কী করে শুরু হল ব্যাপারটা? অবশ্যই ঝগড়া থেকে। এবং এরকম ঝগড়া এই দশ বছরে অন্তত হাজারবার আমাদের মধ্যে হয়েছে। আর সবচেয়ে দুঃখের বিষয়, সবসময়েই আমাদের ঝগড়ার বিষয় ছিল একটাই টাকা!
তুমি লিখতে পারো কি না পারো, সেটা আমার জানার দরকার নেই। হতে পারে, তুমি হয়তো ঘ্যাম লেখক! তোমার প্রতিভার দাম অপোগণ্ড প্রকাশকরা দিতে পারছে না। কিন্তু তাই বলে সংসার খরচের কথা ভুলে বসে থাকলে তো চলবে না। আমার প্রশ্ন হল একটাই : রোজকার খরচের টাকা আসবে কোত্থেকে?
বক্তব্যটা যে রীণার, সেটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।
তবুও মিনমিনে প্রোটেস্ট করেছি আমি : কীসের রোজকার খরচ? বরং বলো অদরকারি খরচ! যেসব জিনিস আমাদের কেনার কোনও দরকার নেই সেসব কিনে ফালতু।
অদরকারি জিনিস? ফালতু খরচ! ব্যস, শুরু হল তৃতীয় মহাযুদ্ধ।
ওঃ, টাকা ছাড়া এ-দুনিয়ায় জীবনের চাকা অচল। টাকাকে হারিয়ে দিতে পারে এমন কিছুই পৃথিবীতে নেই। এখানে টাকাই প্রথম এবং শেষ কথা।
টাকা-টাকা-টাকা…এই অসংখ্য জটিল সমস্যা নিয়ে শান্তিতে দুকলম আমি লিখি কী করে? নতুন ফ্রিজ আর টিভির সেকেন্ড ইনস্টলমেন্টের টাকা বাকি। তার ওপর রীণা নতুন একটা কয়ারের ম্যাট্রেস সমেত খাট কিনতে চায়–জানি না, এইসব প্রবলেম কী করে সম্ভ হবে…।
কিন্তু এত সমস্যা সত্ত্বেও আমি হদ্দ বোকার মতো সমস্যাকে আরও ঘোরালো করে তুলেছি।
সেদিন কি অমনভাবে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে না গেলে আমার চলত না? আগে তো কোনওদিন আমি এমন করে রেগেমেগে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাইনি!
আমাদের মধ্যে ঝগড়া হয়েছিল ঠিক কথা, কিন্তু ঝগড়া তো আমরা আগেও করেছি। জানি, ইগোই এর একমাত্র কারণ। এই লম্বা বারো বছরের হ্যাঁ, একডজন বছর!–লেখক-জীবনে লেখা থেকে আমার আয় মাত্র দু-হাজার সাতশো ষোলো টাকা! এবং সেই কারণেই আমাকে এখনও ওই হতচ্ছাড়া স্টেনো-টাইপিস্টের চাকরিটা করে যেতে হচ্ছে। সুতরাং, আমার লেখার ক্ষমতাকে সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ ওর রয়েছে। সেইজন্যেই, সমীর ওর ম্যাগাজিনে যে-চাকরিটা আমাকে দিতে চাইছে, সেটা নেওয়ার জন্যে রীণা রোজই আমাকে তাড়া দিচ্ছে।
সবকিছুই ডিপেন্ড করছে আমার ওপর। স্ট্রেটকাট হার মেনে নিয়ে সমীরের এগিয়ে দেওয়া চাকরিটা নিলেই সব সমস্যা চুকে যায়। অন্তত এখনকার মতো। পার্ট-টাইম কাজও আমাকে আর করতে হয় না। রীণাও শান্তিতে ঘরে বসে আয়েশ-আরাম করতে পারবে।
কিন্তু আমি? আমি করে বসেছি ঠিক উলটো কাজগুলো। মাঝে-মাঝে এইজন্যে নিজেকে ভীষণ গুড ফর নাথিং বলে মনে হয়।
হঠাৎই সুবোধ-সুশীল আমি একদিন বেরিয়ে পড়েছিলাম কৃতান্তের সঙ্গে। কৃতান্ত আমার কলেজ লাইফের বন্ধু। বরাবর কারণবারির ভক্ত। আমি ওসব খাই-টাই না। তাই ওকে সবসময় বারণ করি। আর রেগুলার বারণ করতে করতে ও-ই শালা কখন যেন আমার জলপথে হাতেখড়ি করিয়ে দিয়েছে।
রাগ করে বেরিয়ে গিয়ে আমি কৃতান্তকে ফোন করেছিলাম। তারপর ওর সঙ্গে জোট বেঁধেছিলাম। ও তখন একটা সাউথ ইন্ডিয়ান ফুডের রেস্তোরাঁয় বসে দুটো ইয়াং মেয়ের সঙ্গে গল্প করছিল। তার মধ্যে একজনকে আবার দারুণ দেখতে! সুন্দর তো বটেই। তার সঙ্গে মেশানো ছিল দুষ্টু দুষ্টু ভাব। আর অন্যজন ছিল ফরসা, রোগাটে।
কৃতান্ত বলেছিল, ওরা দুজন ওর বেশ ইন্টারেস্টিং ফ্রেন্ড। রাসেল স্ট্রিটের একটা লেডিজ হস্টেলে থাকে।
ইন্টারেস্টিং ফ্রেন্ড! কে জানে, কৃতান্তর সব উলটোপালটা পাগলা ব্যাপার!
রেস্তোরাঁয় আড্ডা শেষ হলে আমি আর কৃতান্ত জলপথে সাঁতার কাটতে গিয়েছিলাম। তারপর আর কী করেছি মনে নেই। কপাল ভালো যে, রীণা থানায় খবর দেয়নি।
তবে ওই দুষ্টু-দুষ্টু মেয়েটার হাবভাব অনেকটা রীণার মতন লাগছিল–দশ বছর আগে রীণা যেমন ছিল।
না, কাজটা আমি ঠিক করিনি। তাই খুব খারাপ লাগছে। রীণাকে আমি এখনও ভীষণ ভালোবাসি। ভেতরে-ভেতরে সেটা আমি বেশ ভালো করে জানি।
শুক্রবার। বিকেল।
যাক বাবা, রীণা আমাকে ক্ষমা করেছে। আশা করি সব আবার ঠিকঠাক হয়ে যাবে। পরদিন একটু বেলার দিকে বাড়ি ফিরে চোরের মতো মুখ করে বিছানায় গিয়ে বসতেই রীণার ঘুম ভেঙে গেল। ও প্রথমে তাকাল আমার দিকে, তারপর দেওয়াল-ঘড়ির দিকে। ওর ফোলা-ফোলা চোখে-মুখে স্পষ্ট কান্নার ছাপ।
কোথায় ছিলে কাল সারা রাত? ভয় পাওয়া শিশুর গলায় জানতে চাইল ও।
কৃতান্তর সঙ্গে। আলতো গলায় বললাম, ওর বাড়িতে শুয়ে-বসে কাটিয়েছি।
একটা ফোন করতেও ইচ্ছে করল না? ধরা গলায় বলল। আমার দিকে আরও কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর আমার হাতটা নিয়ে গালে চেপে ধরল।
আমাকে ক্ষমা করো। প্লিজ। ভেজা চোখে কান্না-ভেজা গলায় বলল।
মুখ লুকোতে ওর শরীরে মুখ ডুবিয়ে দিলাম ও রীণা, রীণা–আমাকে ভুল বুঝো না, প্লিজ।
আমি সারা রাত কোথায় ছিলাম সে কথা নেশার ঘোরে আমিও ভুলে গেছি। তবে এটুকু মনে আছে, কৃতান্ত ওর দুজন গার্ল ফ্রেন্ডের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। তার মধ্যে একজনকে দেখতে ফ্যান্টা। কী যেন নাম? কী যেন নাম মেয়েটার? নাঃ, মনে পড়ছে না। তবে অন্যজনের নাম ছিল রোজি।
কিন্তু এ কথাটা কিছুতেই রীণাকে বলা যাবে না। ও শুধু-শুধু কষ্ট পাবে। ওকে আমি ভীষণ ভালোবাসি। রাগের মাথায় মানুষ অনেক উলটোপালটা কাজ করে। আমিও তো তাই-ই করেছি– মাত্র একবারের জন্যে। তাও শুধু গল্পগুজব আর কিছু নয়। এটা ওর ক্ষমা করে দেওয়া উচিত।
তা ছাড়া, রীণা ছাড়া আমার কাছের মানুষ আর কে আছে!
কিন্তু কী যেন নাম ছিল ওই মেয়েটার? কৃতান্তর ওই সুন্দর দেখতে গার্ল ফ্রেন্ডের? নয়না? নয়না বোস? তাই কি?
শনিবার। রাত।
আজ সন্ধেবেলা রীণাকে নিয়ে বউবাজারে ফার্নিচারের দোকানে গিয়েছিলাম। নতুন পছন্দসই খাটটা কেনার সময় রীণা আমার কানে কানে বলেছে, একসঙ্গে এতগুলো টাকা খরচ করা কি ঠিক হবে?
সে তোমাকে ভাবতে হবে না। মিষ্টি হেসে জবাব দিয়েছিঃ পুরোনো খাটটার অবস্থাটা দেখেছ! আমি চাই আমাদের ছেলেমেয়েরা ছোটবেলা থেকেই একটু আয়েশ করে ঘুমাক।
দোকানদারের চোখ এড়িয়ে আড়ালে ছোট্ট করে ভালোবাসার শব্দ করল রীণা। বিছানায় গদির ওপর বসে বাচ্চা মেয়ের মতো দুলতে চাইল। বলল, দ্যাখো, কী নরম! বলে আমার হাতটা ধরে বুলিয়ে দিল গদির ওপরে।
সবকিছু আবার ঠিকঠাক চলেছে। শুধু আমার ধারের অঙ্কটা বেড়ে যাচ্ছে, আমার নতুন গল্পটা কেউ কিনতে চাইছে না, আর আমার সাধের উপন্যাসটা মাত্র পাঁচ জায়গা থেকে ফেরত এসেছে। তবে এবার প্রকাশক ভবনকে ওটা ছাপতেই হবে। ওরা অনেকদিন ধরে লেখাটা আটকে রেখেছে। ওদের ওপর ভরসা করেই আমি অপেক্ষায় আছি। বুঝতে পারছি, আমার লেখার দিন ফুরিয়ে এসেছে। শুধু লেখার কেন, সবকিছুরই। দিনের পর দিন, ক্রমশ যেন বুঝতে পারছি, আমি একটা হেরো ঘোড়া হয়ে যাচ্ছি।
অবশ্য, রীণা এখন অনেক ভালো আছে। এইটুকুই যা সান্ত্বনা।
রবিবার। রাত।
আবার গণ্ডগোল! আবার ঝগড়া! কী থেকে শুরু হল, কী নিয়ে শুরু হল, বুঝতেই পারলাম না। ও রাগ করে গোমড়া মুখে বসে আছে। আর রাগে আমার সারা শরীর জ্বলছে। এইরকম অবস্থায় লেখা যায়! লেখা আসে না। রীণা সেটা ভালো করেই জানে।
ইচ্ছে হচ্ছে নয়নাকে ফোন করি। ও অন্তত আমাকে লেখায় উৎসাহ দিয়েছিল। মনে হচ্ছে, সবকিছু ছেড়ে-ছুঁড়ে নেশায় গা ভাসিয়ে দিই, হাওড়া ব্রিজ থেকে লাফ দিয়ে বসি, কিছু একটা করে বসি।
শিশুরা যে সুখী হবে এতে আর আশ্চর্য কী! ওদের কাছে জীবন অনেক সহজ-সরল। একটু খিদে, একটু ঠান্ডা আরামের পরিবেশ, অন্ধকারকে একটু ভয় পাওয়া ব্যস। ওরা জানে না, কষ্ট করে বড় হওয়ার অনেক কষ্ট। জীবন অনেক জটিল হয়ে ওঠে।
একটু আগেই রীণা খেতে ডেকে গেছে। খাওয়ার ইচ্ছে আর নেই। এমনকী বাড়িতেও একমুহূর্ত থাকতে ইচ্ছে করছে না। দেখি, নয়নাকে পরে একটা ফোন করব। শুধু জানতে ইচ্ছে করছে, ও কেমন আছে।
সোমবার। সকাল।
এই ছিল এদের মনে!
উপন্যাসটা আট মাস ধরে আটকে রেখেও ওদের শান্তি হয়নি। পাণ্ডুলিপির আগাপাশতলা জুড়ে চা-সিগারেটের দাগ খোদাই করে দিয়েছে। আর পাঠিয়েছে একটা এক লাইনের চিঠি ও দুঃখিত, এটা পাবলিশ করতে পারলাম না।
হাতের কাছে পেলে আমি ওদের হয়তো খুন করে বসতাম! ওরা জানে না, আমার জীবনের ওপরে ওরা একটা প্রকাণ্ড পাথর আজ চাপিয়ে দিয়েছে।
চিঠিটা রীণার চোখ এড়াল না।
এবার কী করবে ঠিক করলে? বিরক্ত গলায় ও বলল।
মানে? উত্তরে জানতে চাইলাম। অতি কষ্টে গলা মোলায়েম রাখলাম।
এখনও তোমার বিশ্বাস তুমি লিখতে জানো?
ফেটে পড়লাম হ্যাঁ, ওদের কথাকেই তো বেদ-বাক্য বলে মেনে নিতে হবে! ওরা যা বলবে তা-ই ঠিক! আমার লেখার কতটুকু বোঝে ওরা বলতে পারো? রাগে আমার গলা কাঁপছে।
বারো বছর ধরে তুমি লিখছ, কিন্তু কোনও লাভ হল না। তাই না?
আমি আরও বারো বছর ধরে লিখব। দরকার হলে একশো, হাজার বছর ধরে লিখে যাব।
সমীরবাবুর কাগজের চাকরিটা তুমি তা হলে নেবে না?
না, নেব না।
তুমি বলেছিলে, এই উপন্যাসটা যদি না ওতরায় তা হলে চাকরিটা নেবে।
চাকরি আমার একটা রয়েছে তার সঙ্গে পার্ট-টাইম কাজ। সুতরাং যেমন চলছিল তেমনই চলবে।
কিন্তু সেভাবে আমি তো চলতে পারছি না! ও মুখিয়ে উঠল।
রীণা কি আমাকে ছেড়ে বাপের বাড়ি চলে যাবে? যাক। দেখে-দেখে আমিও টায়ার্ড হয়ে পড়েছি। টাকা, টাকা। লেখা, লেখা। আর প্রকাশকদের কাছ থেকে ফেরত, ফেরত, আর ফেরত!
শুধু আমার চালাক-চতুর জীবন জটিলতার প্যাঁচ একের পর এক পেঁচিয়ে জটিলতার এক প্রকাণ্ড জিলিপি গড়ে চলেছে।
তুমি! তোমাকে বলছি! যে এই পৃথিবী, গোটা সোলার সিস্টেমটাকে ক্রমাগত ঘুরিয়ে চলেছে, তাকে বলছি। যদি আমার কথা শুনতে পেয়ে থাকে তা হলে মন দিয়ে শোনো। এই পৃথিবীটাকে একটু অন্তত সহজ-সরল করে দাও। কোনও কিছুতে আমার আর বিশ্বাস নেই। কিন্তু আমার এই ছোট্ট রিকোয়েস্টটা যদি রাখো, তা হলে তুমি যা চাইবে তা-ই দিতে আমি রাজি! শুধু যদি…।
কিন্তু কী লাভ? এ নিয়ে আর মাথা ঘামাব না। শালা, যা হওয়ার হোক!
নয়নাকে আজ রাতে ফোন করব।
সোমবার। সন্ধ্যা।
একটু আগেই নয়নাকে ফোন করতে গিয়েছিলাম। ইচ্ছে আছে শনিবার ওর সঙ্গে দেখা করব। কারণ, শনিবার সন্ধেবেলা রীণা ওর বোনের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে। আমাকে ও যাওয়ার কথা কিছু বলেনি, আর আমিও যেচে সে কথা আর তুলছি না।
কাল রাতেও নয়নাকে ফোন করেছিলাম–ওর বাড়িতে। ওদের বাড়িটা ওয়ার্কিং গার্লস হোস্টেল গোছের। কিন্তু অন্য একটা মেয়ে জানাল, ও বাড়ি নেই।
তাই ঠিক করলাম, আজ ওর অফিসে ফোন করব। সেখানে নিশ্চয়ই ওকে পাওয়া যাবে।
সুতরাং, মোড়ের ইলেকট্রিকের দোকানটায় গিয়ে ফোন গাইডে ওর নাম্বারটা খুঁজতে লাগলাম। হয়তো সেটা আমার মুখস্থ করে ফেলা উচিত ছিল, কিন্তু কী কারণে জানি না, সেটা করা হয়নি। কারণ, হাতের কাছে টেলিফোন ডিরেক্টরি তো সবসময়েই রয়েছে।
ও প্রসাধন না প্রসাধনী নামে একটা ম্যাগাজিনে কাজ করে বলে জানতাম। আশ্চর্য, ম্যাগাজিনের নামটাও আমার ঠিকঠাক মনে নেই। হয়তো তেমনভাবে ব্যাপারটা কখনও ভেবে দেখিনি।
অবশ্য ওর অফিসটা কোথায় সেটা আমার বেশ মনে আছে। মাসকয়েক আগে একদিন অফিস থেকে ওকে আর কৃতান্তকে এমব্যাসিতে খাওয়াতে নিয়ে গিয়েছিলাম। মনে পড়ছে, রীণাকে বলে বেরিয়েছিলাম ন্যাশন্যাল লাইব্রেরিতে যাচ্ছি। স্টাডি করতে।
নয়নার অফিসের টেলিফোন নাম্বারটা বহুদিনের অভ্যাস থেকে জানি–ফোন-গাইডের ডানদিকের পাতার ওপরে কোনায় থাকে বারবার সেটাই দেখে এসেছি। বহুবার ওকে ফোন করেছি, কখনও জায়গাটা পালটে যায়নি।
কিন্তু পালটে গেছে আজ।
ফোন-নাম্বারটা সেই চেনা জায়গায় নেই!
প্রসাধন দিয়ে শুরু এমন যে-কটা শব্দ পেলাম সবকটাই বাঁ-পাতার নীচে, বাঁ-দিকে। এতদিন যা দেখে এসেছি, ঠিক তার উলটো।
সেই পাতায় চোখ বুলিয়ে এমন কোনও নাম চোখে পড়ল না যেটা স্মৃতিকে উসকে দেয়। অন্যান্য দিনের মতো, ও, এই তো! মনে-মনে বলে দরকারি ফোন-নাম্বারটা আজ খুঁজে পেলাম না।
খুঁজে চললাম। পাতার পর পাতা উলটে চললাম, কিন্তু প্রসাধনী নামে কোনও পত্রিকার নাম আমার চোখে পড়ল না। অবশেষে মনকে বোঝালাম, ওটা প্রসাধনী নয়, প্রসাধন হবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও একটা খটকা মনের মধ্যে রয়ে গেল। কেউ যেন বলতে লাগল, তোমার কোথাও ভুল হচ্ছে।
যাকগে, পরে অন্য আর-একটা দোকান থেকে ট্রাই করব।
আমি..থাক লেখাটা পরে শেষ করব। রীণা এইমাত্র খেতে যাওয়ার জন্যে ডাক দিয়ে গেল। দেরি হলে হয়তো আবার নতুন কোনও ঝামেলা হবে।
পরে।
তৃপ্তি করে খেলাম। সত্যি, রীণা রান্নাটা করতে জানে। ইশ, মাঝে-মাঝে ওই টুকরো অশান্তিগুলো যদি না থাকত! জানি না, নয়না এরকম রান্না করতে পারে কি না।
খাওয়া-দাওয়ার পর একটু হালকা হলাম। বুঝলাম, আমার মন শান্ত করার জন্যে মাঝে এই সময়টুকু দরকার ছিল। কারণ, ওই টেলিফোন নাম্বারের পিকিউলিয়ার ব্যাপারটা আমার ভালো লাগেনি। বরং আমাকে বেশ ধাক্কা দিয়েছে।
আজ আমার অফিস ছুটি, কিন্তু নয়নার পত্রিকা-অফিস খোলা। রাস্তায় বেরিয়ে ওকে একবার ফোন করলে হয়!
কিন্তু প্রসাধনী, না কি প্রসাধন?
অবশেষে প্রসাধন-এর নাম্বারটা ফোন গাইড থেকে খুঁজে বের করে ডায়াল করলাম। একজন মহিলা ও-প্রান্তে রিসিভার তুললেন।
প্রসাধন পত্রিকা অফিস। সুরেলা কণ্ঠ ভেসে এল।
আমি মিস বোসের সঙ্গে কথা বলতে চাই। চেষ্টা করে গলা স্বাভাবিক রাখলাম।
কার সঙ্গে?
মিস নয়না বোসের সঙ্গে।
এক মিনিট। ও-প্রান্ত থেকে তিনি বললেন। এবং সেই মুহূর্তে বুঝলাম, আমি ভুল নাম্বারে ফোন করেছি। অন্যান্যবার ফোন করামাত্রই যে-মেয়েটি ফোন ধরত, সে দিচ্ছি বলে সঙ্গে-সঙ্গে নয়নার টেবিলে লাইন দিয়ে দিত।
নামটা কী যেন বললেন? ও-প্রান্ত থেকে ভদ্রমহিলা আবার একই প্রশ্ন করলেন।
মিস নয়না বোস। দেখুন আপনি যখন ঠিক চিনতে পারছেন না, মনে হয়, আমি হয়তো ভুল নাম্বারে ফোন করেছি।
আপনি মিস্টার ঘোষকে চাইছেন না তো?
না, না। সবসময় ফোন করামাত্রই মিস বোসের লাইন পেয়ে যাই। আমারই হয়তো রং নাম্বার হয়েছে। শুধু-শুধু আপনাকে ট্রাক্ল দিলাম। রিসিভার নামিয়ে রাখলাম।
অস্বস্তির পোকাটা লম্বায় বড় হতে লাগল। নয়নার অফিসে আমি এতবার ফোন করেছি যে, আজকের ঘটনাকে মনের ভুল বলে হেসে উড়িয়ে দিতে পারছি না।
সত্যিই ফোন-নাম্বারটা আমার মনে নেই। অথবা, মনে পড়ছে না।
প্রথমটা নিজেকে তেমন আপসেট হতে দিইনি। হতে পারে, এই দোকানের ফোন গাইডটা হয়তো পুরোনো–এখনও পালটানো হয়নি। কে জানে!
সুতরাং, মোড় ছাড়িয়ে বড় ডাক্তারখানাটায় গেলাম, এবং চেক করলাম। না, সেখানেও সেই একই বই।
ঠিক আছে, কাল অফিস থেকে আবার ওকে ফোন করব। কিন্তু এখন ওকে পেলে ভালো হত। বলে দিতাম, শনিবার সন্ধেটা ও যেন শুধু আমার জন্যেই রেখে দেয়। কৃতান্তকে না ডাকে।
হঠাৎ একটা কথা খেয়াল হল। একটু আগেই যে-মহিলার গলা ফোনে শুনলাম, তার গলাটা আমার খুব চেনা। কারণ প্রসাধনীর অফিসে ফোন করে বরাবর এর গলাই আমি শুনে এসেছি।
কিন্তু…নাঃ, সবকিছু যেন গুলিয়ে যাচ্ছে।
মঙ্গলবার। দুপুর।
প্রথম সুযোগেই রীণার আড়ালে বাড়ি থেকে নয়নাকে ফোন করেছি। ওর হস্টেলে।
ও-প্রান্ত থেকে চেনা গলায় উত্তর এসেছে।
আশ্বস্ত হয়ে নড়েচড়ে বসলাম। গত কয়েকমাসে বহুবার বলা কথাগুলোই আবার বললাম, আমি মিস নয়না বোসের সঙ্গে কথা বলতে চাই। নয়না ম্যাডাম।
ধরুন। এক মিনিট।
ওপাশে অনেকক্ষণ সব চুপচাপ। আমার ধৈর্যে টান পড়তে লাগল।
তারপর আবার রিসিভার নড়াচড়ার শব্দ পেলাম। উত্তরও পেলাম।
নামটা কী যেন বললেন? মেয়েটি প্রশ্ন করল।
মিস নয়না বোস, মিস নয়-না বোস, জোরের সঙ্গে বললাম, আগেও আমি ওঁকে বহুবার ফোন করেছি…।
দাঁড়ান, আর-একবার দেখছি।
সুতরাং আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা।
তারপর আবার মেয়েটির গলা শুনতে পেলাম।
সরি, স্যার। এ-নামে এখানে কেউ থাকে না।
কিন্তু বললাম যে, আমি আগেও অনেকবার এখানে ফোন করেছি।
আপনার রং নাম্বার হয়নি তো?
না, না। নাম্বার ঠিকই আছে। এটা সতেরো নম্বর রাসেল স্ট্রিট তো?
হ্যাঁ–।
তা হলে তো ফোন-নাম্বারও ঠিক আছে।
কী জানি মেয়েটির স্বর অপ্রস্তুত, বাট, স্যার, এটা আপনাকে কনফার্ম করে বলতে পারি, ওনামে এখানে কোনও বোর্ডার নেই।
কিন্তু কাল রাতেও তো আমি ফোন করেছিলাম। আপনি বললেন মিস বোস এখন নেই–কোথায় বেরিয়েছেন।
সরি, স্যার, ঠিক মনে করতে পারছি না।
কী বলছেন! আপনার কোথাও একটা মেজর মিসটেক হচ্ছে।
দেখুন, আপনি যদি চান তা হলে আমি আরও একবার খোঁজ করতে পারি। বাট ইউ নো, কোনও লাভ হবে না। কারণ, ও-নামে এখানে কেউ থাকে না, বিশ্বাস করুন।
গত কয়েকদিনের মধ্যে কেউ এ-হস্টেল ছেড়ে চলে যায়নি তো?
গত এক বছরে আমাদের এখানে কোনও রুম খালি হয়নি। জানেন তো, কলকাতায় ঘর পাওয়া কী ঝামেলার।
জানি। রিসিভার নামিয়ে রাখলাম।
ক্লান্ত পা ফেলে ফিরে এসে বসলাম। দেখি রীণা কতকগুলো কাগজপত্র হাতে নিয়ে আমারই দিকে এগিয়ে আসছে। বোধহয় ওর হাবিজাবি কিছু টাইপ করাতে। কাগজগুলো আমার টেবিলে নামিয়ে রেখে ও জানতে চাইল আমি একটু আগে কাকে ফোন করছিলাম।
বুঝলাম, আমার ফোন করার ব্যাপারটা ও কোনওভাবে লক্ষ করেছে।
বললাম, ওই চাকরিটার ব্যাপারে সমীরকে ফোন করেছি।
জানি, এবার রীণার তাগাদায় আমাকে ওষ্ঠাগত প্রাণ হতে হবে, কিন্তু তাড়াতাড়িতে এর চেয়ে ভালো মিথ্যে মাথায় এল না।
চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে কিছুক্ষণ টাইপ করলাম। মন এলোমেলো থাকায় আচ্ছন্নের মতো কাজ করে চললাম।
নয়না বোস নেহাত উবে যেতে পারে না, মনে-মনে ভাবলাম। কোথাও না কোথাও ও আছেই। কারণ, গত কয়েকমাসের ঘটনা তো আর কল্পনা নয়, বাস্তব সত্যি! রীণার কাছে কৃতান্ত আর নয়নার সঙ্গে রেগুলার মিট করার ব্যাপারগুলো গোপন রাখার জন্যে কত মিথ্যেই বলেছি!
হঠাৎই মনে পড়ল, একদিন নয়নার সঙ্গে তো ওর এক বন্ধু এসেছিল–ওর সঙ্গে একই হস্টেলে থাকে! কী যেন নাম মেয়েটির? কী যেন…?
হ্যাঁ, মনে পড়েছে। রোজি…রোজি আচারিয়া।
সুতরাং রীণাকে এড়াতে সিগারেট কিনতে যাওয়ার ছলে বাড়ি ছেড়ে রাস্তায় এলাম। বেরিয়ে এসেই মনে পড়ল, মাস ছয়েক হল সিগারেট খাওয়া আমি ছেড়ে দিয়েছি–ডাক্তারের বারণ। রীণাও সেটা জানে। নাঃ, ক্রমশ একরাশ কমজোরি মিথ্যের জালে আমি জড়িয়ে পড়ছি।
সুবিধে মতো জায়গা বেছে নিয়ে ফোন করতে দেরি হল না।
উত্তর দিল সেই একই মেয়ে।
একটু উদ্ধতভাবেই প্রশ্ন করলাম, রোজি আচারিয়া আছেন?
একমিনিট…ধরুন।
বুকের ভেতরটা হঠাৎ কেমন ফাঁকা ঠেকল। আগে কখনও ফোন করার পর একমিনিট ধরতে হয়নি। সঙ্গে-সঙ্গেই যাকে চাই তাকে পেয়ে গেছি। তা ছাড়া কৃতান্তর কাছেই শুনেছি, নয়না আর রোজি কম করে দু-বছর ধরে ও-বাড়িতে আছে।
সরি, একটু পরেই মেয়েটির গলা শুনতে পেলাম, ও-নামে এখানে কেউ থাকে না।
ওঃ গড!
কী হল? কিছু বলছেন?
নয়না বোস, রোজি আচারিয়া, কেউই এখানে থাকে না?
আপনিই কি একটু আগে ফোন করেছিলেন?
হ্যাঁ।
দেখুন, এরকম বাজে ইয়ার্কি করে…।
ইয়ার্কি! কাল রাতেই আপনি আমাকে বলেছেন, মিস বোস এখন বাড়িতে নেই, কোনও খবর দেওয়ার থাকলে আমি আপনাকে দিতে পারি। আমি পরে ফোন করব বলে ছেড়ে দিয়েছি। আর এখন আপনি বলছেন, ও নামে এখানে কেউ থাকে না!
দেখুন, জানি না কীভাবে আপনাকে বোঝাব। কাল রাতের সব ফোন আমিই ধরেছিলাম, কিন্তু আপনার ফোনটার কথা আমি ঠিক মনে করতে পারছি না। যদি বলেন, তা হলে আর-একবার খোঁজ করতে পারি!
না, থাক দরকার নেই। রিসিভার নামিয়ে রাখলাম।
তারপর ফোন করলাম কৃতান্তকে। ওকে বাড়িতে পেলাম না। ওর স্ত্রী, কামিনী, বলল, কোথায় যেন বেরিয়েছে। কোথায় গেছে জিগ্যেস করতে জবাব পেলাম, বোধহয় ছাইপাঁশ গিলতে।
ফোন নামিয়ে রেখে বুঝলাম, আমি ভয় পেয়েছি।
মঙ্গলবার। রাত।
আজ রাতে রীণা পাশের ফ্ল্যাটে গল্পগুজব করতে গিয়েছিল। সেই সুযোগে ঘর থেকেই ফোন করলাম কৃতান্তকে। জিগ্যেস করলাম রোজির কথা।
কে?
রোজি, রোজি।
কে রোজি? ও জানতে চাইল।
শালা, তুই ভালোভাবেই জানিস কোন রোজি! ন্যাকামো হচ্ছে।
কী ব্যাপার? তুই কি ঠাট্টা করছিস নাকি? কৃতান্ত রুক্ষ স্বরে প্রশ্ন করল।
নকশা ছেড়ে পথে আয়। কী ইয়ার্কি করছিস!
একটা প্রশ্নের স্পষ্ট জবাব দে দেখি! বলল কৃতান্ত, এই রোজি-টা কে?
রোজি আচারিয়াকে তুই চিনিস নানয়নার ক্লোজ ফ্রেন্ড?
না। কে সে?
তুই কোনওদিন রোজি, নয়না বোস আর আমার সঙ্গে কোথাও যাসনি?
নয়না বোস! কী উলটোপালটা বকছিস!
নয়না বোসকেও তুই চিনিস না?
না। চিনি না। আর তোর এই বেয়াড়া জোক কিন্তু এবার তেতো হয়ে উঠছে। জানি না তোর মতলব কী, কিন্তু এবার দয়া করে ক্ষান্ত দে। তুই ভালোভাবেই জানিস, আমরা দুজনেই…।
শোন! রিসিভারে মুখ লাগিয়ে চিৎকার করে উঠলাম তিন সপ্তাহ আগে শনিবার রাতে তুই কোথায় ছিলি?
এক মুহূর্ত ও চুপচাপ রইল। তারপর বলল, কেন, সে-রাতে আমি আর তুই সাকিতে একটু ইয়ে খেতে গিয়েছিলাম। মনে নেই?
হ্যাঁ, মনে আছে। তবে তার আগে নয়না আর রোজির সঙ্গে আমরা কিছুক্ষণ ম্যাড্রাস টিফিন-এ বসে আড্ডা দিয়েছিলাম, তোর মনে নেই?
না তো! আমাদের সঙ্গে তো আর কেউ ছিল না।
কোনও মেয়ে ছিল না? নয়না? রোজি?
ওহহো, আবার সেই এক কথা। হয়রান সুরে বলল কৃতান্ত, আচ্ছা, কী ব্যাপার বল তো? কী হয়েছে তোর?
মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করে উঠল। পাশের দেওয়ালে হাত রেখে নিজেকে সামলে নিলাম।
উঁহু কিছু হয়নি– নীচু গলায় জবাব দিলাম।
তোর শরীর ঠিক আছে তো? কথাবার্তা শুনে তো মনে হচ্ছে ভীষণ আপসেট হয়ে পড়েছিস!
ফোন নামিয়ে রাখলাম। সত্যিই আমি আপসেট হয়ে পড়েছি। মনে হচ্ছে যেন সাতদিন ধরে উপোস করছি, অথচ সারা পৃথিবীতে মুখে দেওয়ার মতো কোনও খাবার নেই। কেউ যেন একরাশ হাওয়া আমার শরীরে, মাথায়, জোর করে ঢুকিয়ে দিচ্ছে–দিয়ে চলেছে।
আমার হলটা কী?
বুধবার। বিকেল।
রোজি আর নয়না সত্যি-সত্যিই উধাও হয়ে গেছে কি না, সেটা যাচাই করে দেখার একটাই মাত্র পথ রয়েছে।
নয়নার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়েছিল কলেজের এক বন্ধুর মারফত সুধাকর…সুধাকর নন্দী। সুধাকরের বাড়ি ছিল ওদেরই পাড়ায় হিন্দুস্থান পার্কে। নয়না যে পরে আস্তানা বদল করে রাসেল স্ট্রিটে এসেছে তা জানতাম না। জেনেছি কৃতান্তকে সঙ্গে নিয়ে সেই সন্ধেবেলা ওর সঙ্গে সেকেন্ড টাইম দেখা হওয়ার পর। সুধাকর প্রথম আলাপ করিয়ে দেওয়ার সময় বলেছিল, নয়না কিন্তু খুব ইন্ডিপেন্ডেন্ট আর জেদি। তার ওপর একটু খামখেয়ালি টাইপ…।
সেইজন্যেই হয়তো এতদিন পরেও ওর নাম আর মুখ আমি ভুলিনি। কে জানে, হয়তো পরে বাবা-মায়ের সঙ্গে ঝগড়া-টগরা করে হস্টেলে গিয়ে উঠেছে।
সুধাকরের সঙ্গে কলেজের পর যোগাযোগ নেই আজ বহুবছর। তার মেইন কারণ, পড়াশোনা শেষ করে ও চাকরি নিয়ে দিল্লি চলে গিয়েছিল। আর যাওয়ার আগে দিল্লির ঠিকানা ও আমাকে দিয়ে যেতে ভোলেনি।
এত সব ভাবনাচিন্তার পর এই কথাটাই মনে আসে ও নয়না আর রোজির ব্যাপারটা মোটেও আমার কল্পনা নয়। আমি জানি ওরা রিয়েল–অন্তত একদিন ছিল।
সুতরাং ঠিক করলাম, আজ সুধাকরকে একটা ফোন করব। বলব, কী হয়েছে। ওকে রিকোয়েস্ট করব, নয়না সম্পর্কে কিছু খোঁজখবর নিয়ে আমাকে জানাতে, যাতে আমি এই মিস্ট্রিটাকে হালকা রসিকতা অথবা কাকতালীয় বলে মেনে নিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারি।
তাই সুধাকরের ঠিকানা আর ফোন-নাম্বার লেখা ডায়েরির পাতাটা খুললাম।
ফোন-নাম্বার তো দূরের কথা, সুধাকরের নাম-ঠিকানাও ডায়েরির পৃষ্ঠা থেকে উধাও হয়ে গেছে।
আমি কি পাগল হয়ে গেলাম? আমি শিয়ের যে, নাম-ঠিকানাটা এখানেই লেখা ছিল। একটা রেস্তোরাঁয় বসে যেদিন ওর ঠিকানা আর ফোন-নাম্বার ডায়েরিতে টুকেছি সেদিনটা এখনও আমার স্পষ্ট মনে আছে। পেনের মুখটা ফাটা ছিল বলে কয়েক ফোঁটা কালিও পাতাটায় পড়ে গিয়েছিল– আমার ভালো করে মনে আছে।
আর এখন? পাতাটা নিষ্কলঙ্ক, সাদা!
ওর নাম আমার মনে আছে, মনে আছে ওর চেহারা, ওর কথা বলার ভঙ্গি, আমাদের কলেজ-জীবনের কীর্তিকলাপ, অফ পিরিয়ডে আমাদের আড্ডার রমেটিরিয়াল–সব মনে আছে।
একবার গরমের ছুটিতে একটা চিঠিও সুধাকর আমাকে দিয়েছিল। ঘটনাচক্রে কৃতান্ত তখন ছিল আমার বাড়িতে আমার সঙ্গে গল্প করছিল। চিঠিটা রসিকতা করে গালা দিয়ে সিলমোহর করে দিয়েছিল সুধাকর। সিলমোহরে ছিল ওর নাম-লেখা আংটির উলটো ছাপ। আর চিঠির ওপরে লালকালি দিয়ে লেখা ছিল একান্ত গোপনীয়। ফচকেপনার একেবারে চূড়ান্ত।
সেই চিঠিটা খুলে দেখি তো!
আশ্চর্য! যে-ড্রয়ারে চিঠিটা বরাবর থাকত সেখান থেকে হঠাৎই যেন উধাও হয়ে গেছে।
এ ছাড়া কলেজ ক্যাম্পাসে ফ্রেশার্স ওয়েলকাম-এ তোলা আমাদের দুজনের ফটোও আমার কাছে ছিল। ছবিটা আমার অ্যালবামে সযত্নে সাঁটা ছিল–এখনও আছে। তাই ঝটপট আলমারি খুলে অ্যালবামটা বের করলাম। পাতা উলটেপালটে সেই ফটোটার পাতায় পৌঁছে গেলাম।
কিন্তু…হে ভগবান! সে-ছবিতে সুধাকরের চিহ্নমাত্র নেই। আমার ডানহাত, যেটা ওর কাঁধে রাখা ছিল, সেটা এখন শূন্যে ঝুলছে। সুধাকর যেখানে ছিল, সেখানে এখন দেখা যাচ্ছে পেছনের কলেজ-বাড়ির পোরশান।
আরও খোঁজখবর করতে আমার ভয় করছে। আমি কলেজে চিঠি লিখে অথবা দেখা করে সুধাকরের কথা জিগ্যেস করতে পারি, প্রশ্ন করতে পারি সুধাকর নন্দী নামে কেউ ওই কলেজে কখনও পড়েছে কি না।
কিন্তু সেটুকু করতেও আমি কেন জানি না ভীষণ ভয় পাচ্ছি।
বৃহস্পতিবার। বিকেল।
আজ মিশন রো-তে সমীরের পত্রিকা অফিসে গিয়েছিলাম। ওর সঙ্গে দেখা করেছি। আমাকে দেখে ও ভীষণ অবাক হল। জানতে চাইল, ওর পত্রিকা অফিসে আমার পদধুলি পড়ার কারণ।
তুই আমার অফার করা চাকরিটা নিতে এসেছিস, এ-কথা বলিস না–বিশ্বাস করব না। ও ঠাট্টা করে বলল।
আমি জিগ্যেস করলাম, সমীর, কখনও নয়না নামে কোনও মেয়ের কথা আমার মুখে শুনেছিস?
নয়না? উঁহু, মনে তো পড়ছে না।
প্লিজ, সমীর একটু মনে করে দেখ! আমি ওর নামটা অন্তত একবার হলেও তোকে বলেছি। মনে আছে, যেদিন আমি, তুই, আর কৃতান্ত অলিম্পিয়া-তে গিয়েছিলাম? সেইদিনই বোধহয় ওর কথা তোকে বলেছি।
বলেছিস? আমার কিন্তু একদম মনে পড়ছে না বিশ্বাস কর। ও বলল, কেন, কী হয়েছে মেয়েটার?
ওকে আমি খুঁজে পাচ্ছি না। আর কৃতান্ত হারামজাদা সরাসরি মেয়েটার কথা ডিনাই করে বলছে, সাতজন্মে ও নাকি ওর নাম শোনেনি।
সমীর হতভম্ভ হয়ে পড়ায় কথাগুলো স্পষ্ট করে আবার রিপিট করলাম।
তখন ও বলল, কী ব্যাপার রে? তুই বিয়ে করা মরদ অন্য মেয়ের এত খোঁজ নিচ্ছিস।
না রে, অন্য কিছু নয়, স্রেফ বন্ধু। ওকে বাধা দিয়ে বললাম, আমার কলেজের এক বন্ধুর সোর্সে ওর সঙ্গে আমার পরিচয়। উলটোপালটা কিছু ভাবিস না।
ঠিক আছে, ঠিক আছে, ওসব বাদ দে। এখন বল, আমাকে কী করতে হবে।
আমি ওদের খুঁজে পাচ্ছি না–মানে, নয়নার সঙ্গে ওর এক বন্ধুও ছিল। ওরা একেবারে উধাও হয়ে গেছে। এমনকী ওরা যে-কোনওদিন এই পৃথিবীতে ছিল, তাও আমি এস্টাবলিশ করতে পারছি না।
সমীর কাধ ঝাঁকালঃ হ্যাঁ, তাতে কী হয়েছে? তারপর জানতে চাইল ব্যাপারটা রীণা জানে কি না।
আমি প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলাম।
কাগজে খোঁজ চেয়ে অ্যাড দিবি নাকি? সমীর আবার খোঁচাল আমাকে? নাকি পুলিশে যাবি?
এরপর আর কিছু বলার নেই।
একটু পরে ওর অফিস ছেড়ে বেরিয়ে এলাম। ও বড় বেশি ইন্টারেস্ট দেখাচ্ছিল। এর ফলে কী হবে বেশ বুঝতে পারছি। সমীর ওর বউকে বলবে। ওর বউ বলবে রীণাকে–এবং অ্যাটম বোম।
বাড়ি ফেরার পথে একটু অদ্ভুতভাবেই মনে হল, আমি নিজেও একটা অস্থায়ী জিনিস।
বিছানায় গা এলিয়ে দিতে গিয়ে সেই অদ্ভুত চিন্তার ভয়ংকর অর্থটা আমাকে গ্রাস করল। আর সেইসঙ্গে মনে হল, আমি যেন হাওয়ায় গা ভাসিয়ে দিয়েছি।
ইলেকট্রিক শক খেয়ে উঠে বসলাম। আমি কি পাগল হতে চলেছি? নইলে সঙ্গে-সঙ্গেই বা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ব কেন? রাস্তায় চলা এক প্রৌঢ়কে ইচ্ছে করে শুধু-শুধুই বা ধাক্কা মারব কেন? আমি বোধহয় জানতে চাইছিলাম, লোকটা আমাকে দেখতে পাচ্ছে কি না, আমার অস্তিত্বকে টের পাচ্ছে কি না। লোকটার দাঁতখিচুনি এবং গালাগালিতে আশ্বস্ত হলাম। ইচ্ছে হল, তাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খাই।
সত্যি লোকটার ব্যবহারে আমি কৃতজ্ঞ।
বৃহস্পতিবার। রাত।
সুধাকর নন্দীর কথা ওর মনে আছে কি না সে কথা জানতে কৃতান্তকে আবার ফোন করলাম। বাড়ি থেকেই। উত্তরে ফোন এনগেজড পেলাম। বারবার রিং করে ওই একই পি-পিঁ শব্দ! অগত্যা টেলিফোন কোম্পানির ১৯৯ ডায়াল করলাম। অপারেটার ফোন ধরতেই কৃতান্তর ফোন নাম্বারটা বললাম। কয়েক সেকেন্ড নীরবতা।
একটা ঠান্ডা স্রোত আমার পাকস্থলী থেকে উঠে এল গলা পর্যন্ত। আমি জানি, কী হবে অপারেটারের উত্তর। এবং তাই হল।
মেয়েটা নরম গলায় জানাল, ওরকম কোনও ফোন নাম্বার নেই।
রিসিভারটা আমার হাত থেকে খসে পড়ল মেঝেতে।
শব্দ পেয়ে রান্নাঘর থেকে ছুটে এল রীণা। অপারেটর তখনও হ্যালো, হ্যালো বলছে।
তাড়াতাড়ি রিসিভারটা তুলে জায়গামতো রাখলাম।
কী হয়েছে? রীণা জানতে চাইল।
আমার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। জবাব দিলাম, কিছু না, রিসিভারটা হাত থেকে পড়ে গিয়েছিল।
রীণা কয়েক সেকেন্ড অবাক চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে রান্নাঘরে ফিরে গেল।
বিছানায় বসতেই বুঝলাম, আমার হাত-পা ঠকঠক করে কাঁপছে।
কৃতান্ত আর সুধাকরের কথা রীণাকে বলতে আমার ভয় করছে।
ভয় করছে, কারণ যদি ও হঠাৎ বলে বসে, সাতজন্মে ওদের নাম ও কখনও শোনেনি!
শুক্রবার।
প্রসাধনী পত্রিকা সম্পর্কে আজ একটু খোঁজখবর করলাম। জানলাম, ওনামে কোনও পত্রিকা নেই– কোনওদিন ছিল না। তা সত্ত্বেও একরোখা মন নিয়ে নয়নার অফিসে গেলাম। বেরোনোর সময় রীণা বারবারই জিগ্যেস করছিল কোথায় যাচ্ছি। কিন্তু আমি কোনও জবাব না দিয়ে বেরিয়ে পড়েছি। আজ এ-রহস্যের সরাসরি হেস্তনেস্ত আমাকে করতেই হবে।
অফিসবাড়িটার একতলায় একরাশ কাঠের নেমপ্লেট লাগানো আগের দিনও প্রসাধনী নামটা সেখানে ছিল কিন্তু আজ আর দেখতে পেলাম না। নেমপ্লেটের জায়গাটা ফাঁকা।
ব্যাপারটা একেবারে আনএক্সপেক্টেড।
বুকের ভেতরটা কেমন ফাঁকা-ফাঁকা ঠেকল, মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠল।
ওই অবস্থাতেই সিঁড়ি ভেঙে উঠতে শুরু করলাম। মনে হল যেন হাওয়ায় গা ভাসিয়ে উড়ে চলেছি।
চারতলায় এসে দাঁড়ালাম। চারপাশের ঘর-দরজা সবই আমার চেনা। এখনও স্রেফ চোখ বুজে আমি বলতে পারি নয়নার অফিস কোন ঘরটায়, কোন ঘরে ও বসে বসত।
কিন্তু দেখলাম, সেখানে একটা ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি রয়েছে।
এখানে একটা ম্যাগাজিনের অফিস ছিল না? রিসেপশনিস্টের কাছে প্রশ্ন রাখলাম।
ঠিক বলতে পারছি না–অন্তত আমার তো মনে পড়ছে না। ইতস্তত করে মেয়েটি বলল। তারপর নিষ্ঠুরভাবে যোগ করল, অবশ্য আমি মাত্র বছর তিনেক এখানে জয়েন করেছি।
বাড়ি ফিরে এলাম। রীণাকে বললাম, শরীর ভালো নেই, আজ আর কোথাও বেরোব না। ও বলল, ভালোই হবে। দুজনে মিলে দিনটা বাড়িতেই কাটিয়ে দেওয়া যাবে। একটু একা থাকার ইচ্ছেয় শোওয়ার ঘরে চলে গেলাম। নতুন চোখে তাকিয়ে রইলাম নতুন কেনা কয়ারের গদিওয়ালা খাটের দিকে।
রীণা ঘরে এসে ঢুকল। যুদ্ধং দেহি দৃষ্টি নিয়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইল।
আচ্ছা, তোমার কী হয়েছে বলো তো? ও জিগ্যেস করল, আমার কি একটুও জানার রাইট নেই?
কিছু হলে তো জানবে! ছোট্ট জবাব দিলাম।
আর মিথ্যে কথা নাই-বা বললে, ও বলল, আমি জানি, কিছু একটা হয়েছে।
ভাবলাম, ওকে সব খুলে বলি। কিন্তু এগোতে গিয়েও কী এক অজানা কারণে থেমে গেলাম। বললাম, আমাকে…আমাকে একটা চিঠি লিখতে হবে।
কাকে?
ভেতরে-ভেতরে বিরক্ত হলেও নিজেকে সামলে নিয়ে শান্ত গলায় বললাম, সমীরকে লিখব।
তা হলে তোমার সমীর-কে আমার শুভেচ্ছা জানিয়ো। আর চাকরির ব্যাপারটা নিয়ে পারলে পজিটিভ কিছু বোলো– ওর গলা ঠান্ডা। অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে রয়েছে আমার দিকে।
উত্তরে কিছু একটা হয়তো বলতাম, কিন্তু তার আগেই ও ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।
জেদ নিয়ে বসলাম। কাঁপা হাতে চিঠিটা লিখতে শুরু করলাম। মনে হল, সমীরকে সবকিছু খুলে বলা দরকার। কারণ, পরপর ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো গোপন করার চরম সীমা ছাড়িয়ে ক্রমশ বিপজ্জনক এলাকায় চলে যাচ্ছে। ফোনে এসব কথা বলা সম্ভব নয়। সামনাসামনি বলতে আরও লজ্জা। তাই চিঠিই একমাত্র পথ।
লিখলাম, কৃতান্ত সম্পূর্ণ উধাও হয়ে গেছে। জানতে চাইলাম কৃতান্তকে ওর মনে আছে কি না।
ক্রমশ আমার কাঁপা হাত স্থির হয়ে এল। সারা শরীরে এতটুকু কাঁপুনি নেই, নেই একবিন্দু ভয়–কিংবা উত্তেজনা। আমি যেন একটা রোবট।
মানুষ যখন মরিয়া হয়ে ওঠে তখন বোধহয় এরকমটাই হয়।
শনিবার।
আমি ছুটি নিয়ে বাড়িতে বসে আছি।
এই অদ্ভুত সিচুয়েশানের জ্বলন্ত প্রমাণ দাখিল করতে কী করা যায় সেটাই মনে-মনে ভাবছিলাম। হঠাৎই মনে হল, ক্যামেরার হেল্প নিলে কেমন হয়? রীণা তো এখনও আছে আমার কাছেই আছে। রয়েছে আমার বেশ কয়েকজন আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব। যদি আমি তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে আমাদের ফটো তুলি এবং সবাইকে এক কপি করে দিয়ে দিই তা হলে সেই হারিয়ে যাওয়া র ঘটনা ঘটার পর তারা আমার কথার সলিড প্রুফ পাবে। বুঝতে পারবে, আমি মিথ্যে বলছি না।
সুধাকর অদৃশ্য হয়েছে, হয়েছে কৃতান্ত। রোজি আর নয়নার খবর তো এখন একশো বছরের পুরোনো। এখনও যদি আমি কাউকে এই অদ্ভুত ব্যাপারটা জানাতে না পারি তা হলে এই পৃথিবী আমাকে ক্ষমা করবে না।
উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়ালাম। বাড়িতে ক্যামেরা নেই। একটা ছিল, সেটা ছোটভাই সাউথ ইন্ডিয়া বেড়াতে যাওয়ার সময় নিয়ে গেছে–এখনও ফেরেনি। ফিরবে কি না জানি না। কিন্তু এই মুহূর্তে একটা ক্যামেরা আর এক রোল ফিল্ম আমার চাই।
সামান্য কিছু মুখে দিয়ে শোওয়ার ঘরে গেলাম। তোশকের নীচ থেকে বের করে নিলাম ব্যাংকের চেকবই আর পাশবইটা। তারপর রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম। এবার সোজা ব্যাঙ্ক। টাকা তুলতে হবে।
ব্যাঙ্কে গিয়ে একটা চেক লিখলাম। একটা ভালো ক্যামেরার কথা মনে রেখে টাকার অঙ্কের জায়গায় লিখলাম বারোশো টাকা। তারপর চেক আর পাশবই জমা দিয়ে টোকেন নিলাম। গিয়ে দাঁড়ালাম ক্যাশ কাউন্টারের সামনে। পরপর টোকেনের ডাক আসতে লাগল–আমারটা ছাড়া।
প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর রীতিমতো অধৈর্য হয়ে ক্যাশে বসে থাকা কর্মচারীটিকে প্রশ্ন করলাম, আমার টোকেনটা এসেছে কি না। উত্তরে যথারীতি নেগেটিভ জবাব পেলাম। সেইসঙ্গে সে কাউন্টারের মুখটা ছেড়ে দাঁড়াতে অনুরোধ করল।
অপমানটা হজম করে প্রথম কেরানিটির কাছে গেলাম, যে আমার পাশবই আর চেক নিয়ে টোকেন দিয়েছিল।
তার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই একটা চাপা গালাগালের শেষ টুকরো আমার কানে এল। লোকটা সপ্রশ্ন চোখে আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল, তারপর তাকাল আমার পাশবইটার দিকে। দু চার পাতা উলটে তারপর বলল, মশায় কি ইয়ার্কি-প্রিয়?
তার মানে? আমার স্বর উঁচু পরদায় উঠল।
সে পাশবইটা আমার হাতে ধরিয়ে দিল, চেকটা ছিঁড়ে ফেলে দিল।
সরে দাঁড়ান, পেছনে আরও লোক রয়েছে। লোকটার নুন মাখানো গলা আমার শরীরে কেটে বসল।
মনে হয় আমি চেঁচিয়েই উঠেছিলাম। নইলে সব লোক ঘাড় ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকাবে কেন?
কী হয়েছে বলবেন তো!
দেখলাম, সামনের টেবিল ছেড়ে আর-একজন কর্মচারী আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছে। চারপাশে ভিড় জমছে।
দ্বিতীয় কর্মচারীটি প্রথমজনের চেয়ে বয়স্ক। সেই কারণেই হয়তো তার গলাও একটু নরম, সহানুভূতি মাখানো।
কী হয়েছে, ভাই, গোলমাল কীসের?
এই ভদ্রলোকটিকে একটু ভদ্রতা শিখতে বলবেন? আমার অপমানিত শরীর কাঁপছে। স্বর কাঁপছে : ইনি আমার চেকটা ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছেন, পাশবই ফেরত দিয়ে দিচ্ছেন–এসবের মানে কী?
কই, দেখি আপনার পাশবইটা। বলে হাত বাড়িয়ে পাশবইটা সে নিল। তারপরই অবাক হয়ে চোখ তুলে তাকাল। একটু হেসে স্পষ্ট গলায় বলল, আপনার পাশবইয়ে একটা কালির দাগ পর্যন্ত নেই ধবধবে সাদা।
ছিনিয়ে নিলাম পাশবইটা। পাগলের মতো পাতা হাতড়ে গেলাম। বুকের ভেতর বুলডোজার চলছে।
পাশবইটাতে ব্যবহারের কোনও চিহ্নমাত্র নেই। কিন্তু…
কিন্তু কী করে এমন হল– আমি প্রায় ডুকরে উঠলাম।
যদি বলেন তা হলে অ্যাকাউন্ট নাম্বারটা আমরা চেক করে দেখতে পারি। সে বলল, আপনি বরং ভেতরে আসুন।
কিন্তু পাশবইয়ে কোনও নম্বরই নেই। সেটা দেখতে আমার ভুল হয়নি। আমার দু-চোখ। ফেটে জল বেরিয়ে এল।
না…তার আর দরকার নেই– আচ্ছন্ন পায়ে ব্যাঙ্কের দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম।
এই যে ভাই, একমিনিট–শুনুন। লোকটির গলা পেছন থেকে ভেসে এল।
আমি ছুটতে শুরু করলাম।
দুদ্দাড় করে সিঁড়ি ভেঙে নেমে এলাম রাস্তায়।
ঘরে পৌঁছে হাঁপাতে লাগলাম। দেখলাম, রীণা নেই। হয়তো পাশের ফ্ল্যাটে গেছে। রীণার ফিরে আসার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম।
এখনও আমি অপেক্ষা করছি, আর দেখছি পাশবইটা। দেখছি লাইন টানা খালি জায়গাটা, যেখানে আমি নিজের নাম সই করেছিলাম। ছক কাটা শূন্য ঘরগুলো–যেখানে জমা দেওয়া টাকার অঙ্ক স্পষ্ট অক্ষরে লেখা ছিল। আমাদের প্রথম বিবাহবার্ষিকীতে রীণার বাবা-মা রীণাকে ঘড়ি কেনার জন্যে চারশো টাকা উপহার দিয়েছিলেন। অফিসের মাইনে থেকে বাঁচিয়ে জমানো দেড়হাজার টাকা। পাঁচশো টাকা। সাতশো টাকা।
সব খালি।
সবকিছুই ক্রমশ খালি হয়ে যাচ্ছে। প্রথমে নাম, তারপর…।
ভাবছি, এখন পর্যন্ত এই–এর পর কী হবে?
পরে।
এখন বুঝতে পারছি।
রীণা এখনও বাড়ি ফেরেনি।
প্রতিবেশীদের কয়েকজনের ফোন-নাম্বার লেখা ছিল। সেখানে ফোন করে জানলাম, রীণা সেখানে নেই।
তখন ওর দু-একজন বন্ধুর বাড়িতে ফোন করলাম। ওদের জিগ্যেস করলাম রীণা ওখানে গেছে কি না। ওরা বলল, আমি হয়তো ভুল নাম্বারে ফোন করেছি, কারণ, রীণা নামে কাউকে ওরা চেনে না। অথচ আমার নাম বলতেই ওরা চিনতে পারল!
হতবাক হয়ে রিসিভার নামিয়ে রাখলাম।
তারপর একের-পর-এক ফোন করে চললাম। আমার মাসতুতো ভাইকে, দিদিকে, রীণার মা-কে, দাদাকে–কোনও উত্তর নেই। শুধু এনগেজড টোন। আমি জানি ১৯৯ নম্বরে ফোন করলে কী জবাব পাব–আগেও পেয়েছি। ওরাও তা হলে কৃতান্ত, নয়না, সুধাকর, রোজিকে অনুসরণ করেছে?
রবিবার।
জানি না এখন কী করব। সারাদিন জানলার ধারে বসে রাস্তার লোক চলাচল দেখেছি। দেখেছি এই আশায়, যদি চেনা কেউ আমার চোখে পড়ে। পড়েনি। প্রতিটি পথচারীই আমার অচেনা– যেমন ছিল গত রাতে টিভির পরদায় দেখা প্রতিটি শিল্পী, অভিনেতা। এমনটা আগে কখনও হয়নি।
এখন বাড়ি ছেড়ে বেরোতে আমার ভয় করছে। থাকার মধ্যে শুধু এটাই আছে। আর আছে আমাদের ফার্নিচার, জামাকাপড়।
শুধু আমার জামাকাপড়। রীণার পোশাকের আলমারি একেবারে কঁকা। আজ ভোরে ঘুম ভাঙতেই আলমারিটা খুলে দেখেছি। আমার ভয়টাই সত্যি হয়েছে।
সত্যি, পুরো ব্যাপারটা যেন ম্যাজিক। প্রত্যেকটা জিনিস কোনওরকম জানান না দিয়েই উধাও হয়ে যাচ্ছে। যেন…।
হাসি পেল। আমার নিশ্চয়ই মাথা…।
ফার্নিচারের দোকানে একবার ফোন করলাম। রোববার বিকেলে ওদের খোলা থাকে। আমার আর রীণার নাম বললাম। বললাম, দিনকয়েক আগে আমরা একটা কয়ারের গদি-ওয়ালা খাট কিনেছি।
ওরা একটু পরেই জানাল, না, ওই নামে কাউকে ওরা কোনও খাট-টাট বিক্রি করেনি।
ফোন করলাম টিভির দোকানে।
না, ও-নামে ওদের কাছ থেকে কেউ ইনস্টলমেন্টে টিভি কেনেনি।
রেফ্রিজারেটারের দোকানেরও সেই এক কথা। বলল, ইচ্ছে হলে আপনি নিজে এসে বিল বই দেখে যেতে পারেন।
ফোন নামিয়ে রেখে আবার জানলার কাছে এসে বসলাম।
ভাবলাম, খড়গপুরে আমার পিসি থাকে, তাকে একটা ফোন করি। কিন্তু ফোন নাম্বারটা কিছুতেই মনে পড়ছে না। আমার নাম-ঠিকানা ফোন নাম্বার লেখা ডায়েরির সব পাতাই সাদা। শুধু মলাটে আমার নামটা বড়-বড় হরফে জুলজুল করছে–অন্তত এখনও।
নাম। শুধু নামটাই এখন আমার শেষ সম্বল। এখন আমি কী করি?
সবকিছুই এত সহজ-সরল যে, আমার করার কিছু নেই। শুধু চুপচাপ বসে আমাকে এর শেষ দেখে যেতে হবে।
আজ আবার অ্যালবামটা নিয়ে বসেছি। দেখেছি সব ছবিই কেমন অদ্ভুতভাবে বদলে গেছে। কোনও ছবিতেই কোনও লোক নেই–শুধু আমি ছাড়া।
রীণার ছবি নেই, আত্মীয়স্বজন কারও ছবি নেই। যাঃ শালা!
আমার বিয়ের ছবিতে গলায় মালা, মাথায় টোপর পরে আমি একাই। একটা রজনীগন্ধার মালা আমার পাশে শূন্যে ঝুলছে।
বিয়ের সময় কৃতান্ত রীণাকে একটা সুন্দর টেবিল-ঘড়ি প্রেজেন্ট করেছিল। তখন সমীর ফটো তুলেছিল। এখন সেই ছবিতে কেউ নেই–শুধু শূন্যে ভেসে থাকা টেবিল-ঘড়িটা ছাড়া।
বুঝলাম, আমার ক্যামেরা কেনার আর কোনও দরকার নেই।
সোমবার। সকাল।
সমীরকে পাঠানো চিঠিটা Not Found ছাপ মারা।
পিওনের সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করেছিলাম, পারিনি। আমি নেমে আসার আগেই নীচতলার ডাকবাক্সে চিঠি ফেলে সে চলে গেছে। জানলা থেকে তাকে দেখেই বুঝেছি, সে আমার সম্পূর্ণ অচেনা। আগে কোনওদিন লোকটাকে আমি দেখিনি।
বাড়ির কাছাকাছি স্টেশনারি দোকানটায় গিয়েছিলাম। দোকানদার আমাকে চিনতে পারল। কিন্তু তাকে রীণার কথা জিগ্যেস করতেই বলল, আর ঠাট্টা করবেন না। আপনি নিজেই কতদিন আমাকে বলেছেন, বিয়ে-ফিয়ে লেখকদের জন্যে নয়। ওই একটি ভুল জীবনে করছি না।
আর একটা মাত্র উপায় আমার হাতে রয়েছে। প্রচণ্ড ঝুঁকি থাকলেও কাজটা আমাকে করতেই হবে। বাড়ি ছেড়ে আমাকে একবার এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে যেতে হবে। সেখানে আমার, রীণার, দুজনেরই কার্ড করা ছিল। অনেকবার রিনিউ-ও করেছি। ওদের কাছে নিশ্চয়ই খাতাপত্র থাকবে, তাতে নিশ্চয়ই আমার সম্পর্কে বেশ কিছু ইনফরমেশান লেখা থাকবে। এই বিপন্ন মুহূর্তে ওরাই আমার একমাত্র ভরসা।
রোজনামচা লেখা এই ডায়েরিটাও সঙ্গে নিচ্ছি। এটা আমি হারাতে চাই না। এটা হারিয়ে গেলে, আমি যে পাগল নই সেটা আমাকে কে মনে করিয়ে দেবে? এই দুনিয়ায় এটাই হবে আমার একমাত্র সান্ত্বনা।
সোমবার।
বাড়িটা হাওয়া হয়ে গেছে। কাছাকাছি একটা রেস্তোরাঁয় বসে আছি।
এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ থেকে ফিরে এসে খানিকটা ফাঁকা জায়গা দেখতে পেলাম। কয়েকটা ছেলে সেখানে খেলা করছিল। ওদের ডেকে জিগ্যেস করলাম, এখানে যে বাড়িটা ছিল তার কী হল। ওরা বলল, ছোটবেলা থেকেই বরাবর এ-মাঠে ওরা খেলছে।
এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে জেনেছি, আমার বা রীণার সম্পর্কে ওরা কিছু জানে না। ওদের কাছে কোনও রেকর্ডও নেই–কোনওদিন ছিল না।
অর্থাৎ, আমি বর্তমানে আর কেউ নই। এখন যেটুকু আমার আছে তা হল এই শরীরটা– আর তার ওপরে জড়ানো পোশাক। আমার অফিসের আইডি কার্ড, ছবি, সব মানিব্যাগ থেকে উধাও হয়ে গেছে।
ঘড়িটাও হাতে আর নেই। সরাসরি কবজি থেকে হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। মনে আছে, রীণা ওটা আমাকে প্রেজেন্ট করেছিল।
ঘড়ির উলটোদিকে খোদাই করে কয়েকটা কথা লেখা ছিল। আমার মনে আছে–এখনও।
তোমাকে– রীণা।
জটিল চিন্তার হাত থেকে মনকে রেহাই দিতে এক কাপ ক–।