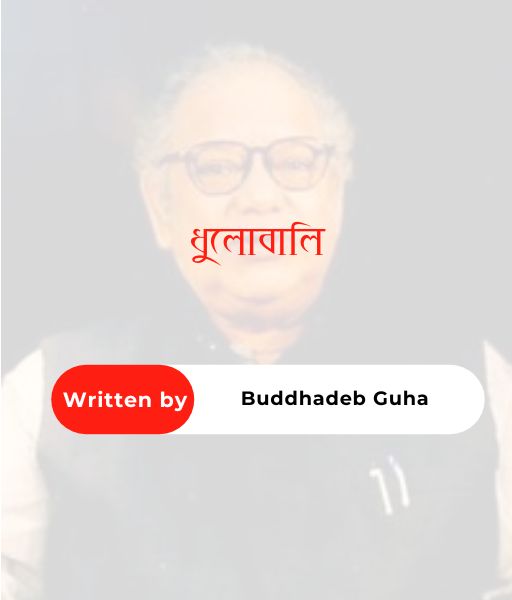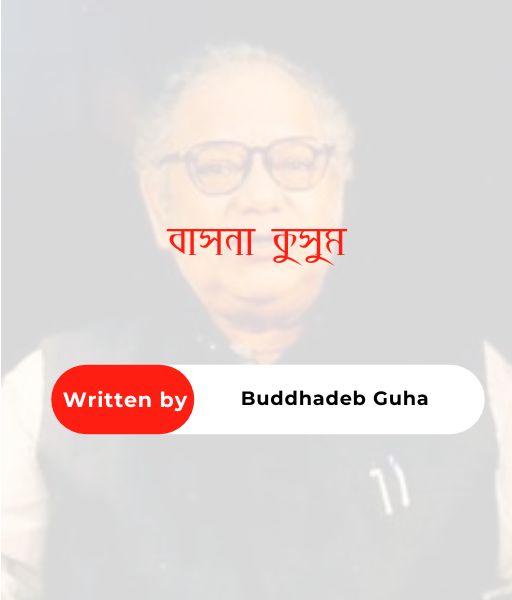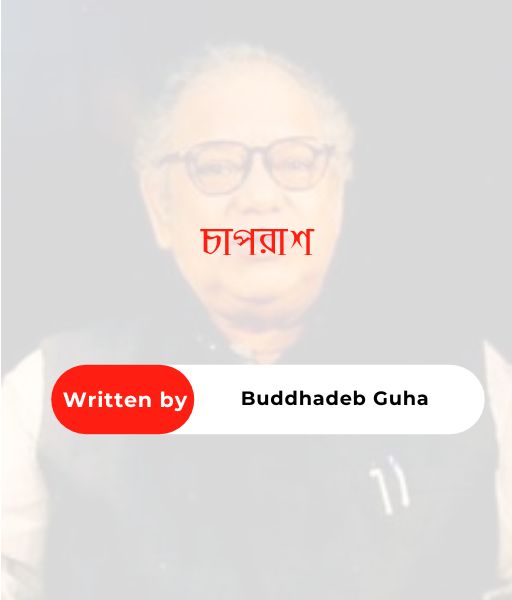সেই প্রথম সকাল
০১.
সেই প্রথম সকাল থেকেই ছুলোয় শিকার হচ্ছে। তিনটি ছুলোয়া হয়ে গেছে। বাকি আছে। একটি। সূর্য এখন চলে পড়েছে পশ্চিমে। সঙ্গে খাবার জল ফুরিয়ে গেছে। খিদেও পেয়েছে। প্রচন্ড।
শেষ ছুলোয়া এক্ষুনি আরম্ভ হল। এই ছুলোয়া শেষ হতে হতে রাত নেমে যাবে।
আমরা তিনজন পঁচাত্তর গজ দূরে বসে আছি পাহাড়টার মাথায়। সামনের মালভূমির ঘন বনের অন্য প্রান্ত থেকে ছুলোয়া করে আসছে গুরবার দল। ছুলোয়ার দলে সবসুদ্ধ জনা তিরিশেক আছে ওরা। সকলেই ক্লান্ত। হয়তো আমাদের চেয়ে বেশিই। তবে, উৎফুল্ল। কারণ, ইতিমধ্যেই শুয়োর মারা পড়েছে তিনটি। তারমধ্যে একটি খুবই বড়ো। প্রকান্ড দাঁতওয়ালা। তা ছাড়া একটি শম্বরও। একটি চিতাবাঘ। মাদি দুটি ময়ূর এবং একটি শজারুও। শুয়োরের মাংস গুরবাদের বড়োই প্রিয়। আর শম্বর তো উপত্যকার তিনটি গাঁয়ের মানুষে ভাগাভাগি, কাড়াকাড়ি করে খাবে। ন-মাসে ছ-মাসে প্রোটিন বলতে তো ওদের এইটুকুই জোটে। দূর দূরান্ত থেকে ওরা ছেলে-মেয়ে-বুড়ো সব সারি বেঁধে পাহাড়-নদী পেরিয়ে হেঁটে আসবে শালপাতার দোনায় করে একটু আঁজলা-ভরা মাংস নিয়ে যাবে বলে। রান্না করবে শুধু নুন দিয়েই। শুধু একটু নোনা হলেই ওদের মনে হবে খাচ্ছে বড়োলোকদের খাবার। ভাত। তাও ন-মাস ছ-মাসে। পরমানন্দে। লবণ আর জীবন, দুঃখে সুখে এদের কাছে সমার্থক।
গুরবা বলেছিল যে, আমরা মালভূমির যে-প্রান্তে বসে আছি তার পশ্চিমের উপত্যকায় নাকি এক বাঙালি বাবু থাকেন। বহত পড়ে লিখে। কবে নাকি শিকার করতেই এসেছিলেন এই অঞ্চলে। গুরবা তখনও জন্মায়ইনি। ওর বাবার কাছেই শুনেছে ও সেই বাঙালিবাবুর আসার গল্প। বাকিটা ওর নিজেরই জানা কথা। তারপর এই বন পাহাড়কে ভালোবেসে সেই বাঙালিবাবু এই জঙ্গলে নাকি থেকে যান। ইচ্ছে করেই জংলি হয়ে যান। বিয়েও করেন স্থানীয় একটি মুণ্ডা মেয়েকে। মুণ্ডা ভাষাও বলেন মুণ্ডাদেরই মতো। তাঁর একটি ছেলেও আছে। একমাত্র সন্তান। তবে তাঁর স্ত্রী মানে সেই মুণ্ডা মেয়েটি মারা গেছেন বছর পনেরো হল। শঙ্খচূড় সাপের কামড়ে।
গুরবাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, সেই বাঙালিবাবু খান কী? মানে, কী করেন? চলে কীসে তাঁর?
গুরবা বলেছিল, উনি তো আর আপনাদের মতো শহুরে বড়োলোক বাবু নন! সেই বাবু যে আমাদের মতোই হয়ে গেছেন। পুরোপুরি বাবু আর নেই। আমরা যেমন থাকি, আমরা যা খাই, আমরা যা করি; জীবিকার জন্যে তিনিও তাই-ই খান, তাই-ই করেন। আমাদের থেকে তাঁকে আর বিশেষ আলাদা করা যায় না।
কত বছর হল আছেন বাঙালিবাবু?
ঠিক বলতে পারব না।
বলেছিল, গুরবা, তবে আমার বাবা আজকে মারা গেছেন কুড়ি বছর। বাবার মুখে শুনেছি, বাবার যখন পনেরো বছর বয়েস, যে বছরে প্রচন্ড খরা হয়েছিল আবার বর্ষাও হয়েছিল একেবারে পৃথিবী ভাসানো, সেই বছরেই বাঙালিবাবু প্রথম এখানে আসেন।
তোর বাবা কত বছর বয়সে মারা যান?।
যে বছর গুণ্ডা হাতিটা বিসপাতিয়ার মাকে পায়ের তলায় চেপটে মারে ডুংরির ওপরে, সেই বছর।
আমি হতাশ হয়ে তাকিয়েছিলাম গুরবার মুখে। সন তারিখের কোনো ধার ধারে না ওরা। বেশ আছে। সময় ওদের কাছে জব্দ হয়ে আছে। থাক।
এবার আস্তে আস্তে ছুলোয়াওয়ালাদের ঢাকঢোল এবং চিৎকার জোর হচ্ছে। গাছে গাছে টাঙ্গি ঠোকার ঠকঠক আওয়াজ। এই মালভূমিতে নাকি বাঘ নেই। বড়ো বাঘ নেই, চিতাবাঘও নেই। জন্তু জানোয়ারের যাতায়াতের সব অলিগলিই গুরবা এবং তার অনুচরেরা খুঁটিয়ে দেখেছে। বাঘ নেই বলছে ওরা, তবে নাকি আছে একদল বাইসন। তাদের সর্দার এতই বুড়ো হয়ে গেছে যে, তার গায়ের রং পেকে একদম বাদামি হয়ে গেছে। সর্দারের মতো সর্দার বটে! গুরবাদের কোনোদিন সাহসই হয়নি তাদের গাদা বন্দুক দিয়ে সেই সর্দারের গায়ে গুলি করার। ওরা বলে, সর্দারের গায়ে গুলি করলে মারাংবুরু চটে যাবেন।
আমার হাতে ফোর ফিফটি-ফোর হান্ড্রেড ডাবল-ব্যারেল রাইফেল। জেফ্রি, নাম্বার টু। একটু আগে ডানদিকের ব্যারেল থেকে সফট-নোজড বুলেটটি বের করে নিয়ে একটি হার্ড নোজড বুলেট পুরে নিয়েছি। আর বাঁ-ব্যারেলের সফট-নোজড বুলেটটি আছে। সর্দারের সঙ্গে যদি মোলাকাত হয়ই তাহলে সামনাসামনিই হবে না পাশাপাশি হবে, তা তো জানা নেই। বসেছি মাটিতেই। তড়িঘড়ি মাচা-টাচা বাঁধা যায়নি। তাই সামনাসামনি হলে তার দু-চোখের মাঝখানে হার্ড-নোজড বুলেট দিয়ে মারব বলেই ঠিক করেছি। আর পাশাপাশি তাকে পাওয়া গেলে, মানে তার ব্রড-সাইড, ঘাড়ে, কী তার উরুর এবং বুকের সংযোগস্থলে সফট-নোজড বুলেট দিয়ে মেরে দেব। সফট-নোজড বুটেল বিধ্বস্ত করে দেবে তার বুক। মারাংবুরুর ভয়ে ওরা জবুথবু হলে হোক, আমরা নই।
উত্তেজনা বাড়ছেই ক্রমশ। আমরা পুবে বসে, পশ্চিমে মুখ করে আছি। সূর্য ডুবতে এখনও কিছু দেরি। তাই হাঁকোয়া শেষ হওয়া অবধি রাইফেলে নিশানা নেওয়ার মতো আলো যে অনেকই থাকবে সে বিষয়ে প্রায় নিঃসন্দেহই। পুবে বসে পশ্চিমে মুখ করে আছি বলেই যতক্ষণ না সূর্য ঘন শালবনের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে উপত্যকার নদীর দিকে গড়িয়ে যায় ততক্ষণ আমার রাইফেলের পাল্লার মধ্যে কোনো জানোয়ার এলে প্রাণ নিয়ে পালাতে পারবে বলে মনে হয় না। তখন বয়েসও খুব কম আমাদের। হাত কারোরই খারাপ নয়। অন্তত অন্যরা তা-ই বলতেন। নিজেদের গুণগান নিজের মুখে কী করে আর করি!
ছুলোয়া এগোচ্ছে। আওয়াজও বাড়ছে। বাঘ নেই বলে কোনো স্টপারও নেই। আমরা অর্ধবৃত্তে বসে আছি। তিনজনই মাটিতে। মোটা মোটা গাছের গুঁড়ির আড়াল নিয়ে। একে অন্যকে দেখতে পাচ্ছি না। তবে, আড়াল নিয়ে বসার আগে কু দিয়ে জানিয়ে দিয়েছি কে কোথায় বসে আছি; যাতে পাশ থেকে একে অন্যের ওপরে ভুলক্রমে কেউ গুলি না চালায়।
সময় যতই এগোচ্ছে শেষ-পৌষের কর্কশ শীত দু-কাঁধের ওপর তার অদৃশ্য শীতল থাবা দু-খানিই যেন ধীরে ধীরে নিঃশব্দে বসিয়ে দিচ্ছে। কান দুটো ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। শিরশির করছে নাকের ডগা। হাতের আঙুলের হাড়গুলো একটু উষ্ণতা খুঁজছে।
একঝাঁক বন-মোরগ দিনের শেষ-আলোয় যেন লাল-সোনালি রঙের আবির ছুঁড়ে দিয়ে কঁক-কঁকিয়ে মালভূমির মধ্যে থেকে কিছুটা দ্রুতপায়ে দৌড়ে এসে, তারপর কিছুটা উড়েই মুহূর্তের মধ্যে চোখের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল আমার বাঁ-পাশ দিয়ে। শেষ ছুলোয়ায় সেই বাইসনের দলের সর্দার ছাড়া আর কোনো কিছুকেই গুলি করব না, এমনই ঠিক করে নিয়েছিলাম আমরা।
হঠাৎ-ই একটা মাদি কোটরা হরিণ হিস্টিরিয়া-রোগিণীর মতো হিককা তুলে ডাকতে ডাকতে আমার প্রায় তিরিশ-চল্লিশ গজ নীচের পাহাড়ের মধ্যের একটি জঙ্গলাবৃত ফাটল বেয়ে মালভূমির দিকে তরতরিয়ে নেমে গেল। বোধ হয় আমাকে দেখেই তার এই ভয়। ভাবলাম আমি। অনড় হয়ে বসে থাকা সত্ত্বেও সে দেখে ফেলল কী করে আমাকে? তার মানে, ভালো আড়াল নিয়ে বসা হয়নি।
গুরবার ছুলোয়াকারীর দল এবার একেবারেই কাছে চলে এসেছে। ঘন বনের ফাঁকে ফাঁকে একটু পরেই মালকোঁচা-মারা ধুতি আর রঙিন মলিন শার্ট পরা তাদের রুখুসুখু চেহারাগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠবে! ছুলোয়াওয়ালাদের সম্মিলিত নানারকম আওয়াজে মালভূমির চতুর্দিকের বন গমগম করে উঠছে। পাহাড়তলির বন থেকেও সহস্র পাখির বেলা-শেষের উত্তেজিত চিৎকার, ছুলোয়াওলাদের মিশ্র আওয়াজের সঙ্গে মিলেমিশে গিয়ে মাথার মধ্যে একেবারে ধাঁধা ধরিয়ে দিচ্ছে। ঠিক সেই সময়েই, প্রচন্ড উত্তেজনা এবং প্রত্যাশার মধ্যে বাইসনের সর্দার নয়, একটি ছোটোখাটো গোবেচারি খরগোশ কান উঁচু করে লাফাতে লাফাতে আমাদের সামনে বেরিয়ে গুরবা এবং তার সঙ্গীদের সমস্ত আয়োজনকে পন্ড করে এবং আমাদের সকলের ঠোঁটেই হাসির আভাস ফুটিয়ে বড়ো বড়ো ঘাসের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। একেই বলে অ্যান্টি ক্লাইম্যাক্স!
আরও একটু দেখলাম, ধৈর্য ধরে। কারণ, অসম্ভবকে সম্ভব করেই হঠাৎ বাঘ বা চিতা ছুলোয়ার ঠিক শেষমুহূর্তেই ছুতোয়াওলাদের পায়ের একেবারে সামনাসামনি আসে। অপ্রত্যাশিত মুহূর্তে আত্মপ্রকাশকরে চমকে দেয়।
আমরা দাঁড়িয়ে উঠে একত্রিত হতেই গুরবা তার বিফলতার কষ্টকে অস্বীকার করতে চেয়ে তামাক আর চুটটা খাওয়া দাঁত বের করে হেসে বলল, শাল্লা, খারহা। মানহুশ!
মানে, শালা খরগোশ। এবং অত্যন্তই অপয়া। খরগোশ বেরোলে আর কোনো জানোয়ার পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। শিকারের ব্যাপারে এক এক জায়গায় জংলিদের এক এক রকম কুসংস্কার থাকেই।
শুভেন শুধোল, বাংলোতে পৌঁছোতে কোন রাস্তা দিয়ে গেলে শর্টকাট হবে রে গুরবা?
হাঁকাওয়ালারা গোল হয়ে দাঁড়িয়ে কেউ চুটটা খাচ্ছিল, কেউ বা দু-হাতে খৈনি ডলছিল। তারই মধ্যে গুরবা বলল, সব রাস্তাই সমান। তবে, যতটুকু আলো আছে এতে পাকদন্ডী দিয়ে জোরে খুব তাড়াতাড়ি যদি আমরা নেমে যেতে পারি তাহলে বাংলোয় পৌঁছে যাব অন্ধকার হবার ঠিক পরপরই। ওরা পরে আস্তে আস্তে শিকারগুলো বয়ে নিয়ে আসবে মশাল জ্বেলে, বাংলোয়।
শুভেন বলল, অন্য শিকার বাংলোয় আনবার দরকার নেই। খালি চিতাটা এবং একটা ময়ূর যেন বাংলোয় নিয়ে আসে। তারপর আমার দিকে চেয়ে বলল, চল। বহুদিন পর আজকে ময়ূরের বার-বি-কিউ খাওয়াব তোদের। আমি যতক্ষণ তোদের খাবার তৈরি করব, ততক্ষণে তুই আর জ্যোতি মিলে চিতাটাকে স্কিনিং করে ফেল।
জ্যোতি বলল, এটাকে চেন্নাই-এ ভ্যান-ইনজেন অ্যাণ্ড ভ্যান-ইনজেন-এই পাঠাব ভাবছি, ট্যানিং করাবার জন্য।
চিতাটা জ্যোতিই মেরেছিল। ওরই ট্রফি। সুতরাং ও যেখানে খুশি ট্যান করাতে চায়, করাক। আমি বললাম, মনে মনে।
কিন্তু শুভেন বলল, আমাদের কলকাতার পুরোনো কাথবার্টসন অ্যাণ্ড হার্পার কী দোষ করল?
বললাম, বুড়ো ফ্লেভিয়ান সাহেব তো মারা গেছেন। এখন কি আর সেই পুরোনো কাথবার্টসন হার্পার আছে?
তাতে কী! শুভেন বলল। ছেলেরাও ইকুয়ালি ভালো। তা ছাড়া হালদারবাবু, ওঁদের পুরোনো ম্যানজার তো আছেনই! কলকাতায়ই নিয়ে চল। কোথায় চেন্নাই-টেন্নাই পাঠাবি, শুঁটকি মাছের গন্ধ হয়ে যাবে তোর চিতার চামড়ায়।
শুভেন নিমরাজি হয়ে বলল, দেখি।
গুরবার কথামতোই পাকদন্ডী ধরে ও আগে আগে চলল।
একফার্লং মতো গিয়েই পাদদন্ডীটা পাহাড় পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে উপত্যকায় গিয়ে নেমেছে। যেখানে আমাদের ডেরা। ফরেস্ট-বাংলো।
একফার্লং পথও আমরা যাইনি ঠিক সেই সময়েই দীর্ঘদেহী, একমাথা সাদা-চুল এবং মুখভরতি দাড়ি-গোঁফওয়ালা, মালকোঁচা-পরা ধুতি এবং তার ওপর ইস্ত্রিবিহীন সাজিমাটি দিয়ে কাঁচা বুক-খোলা শার্ট পরা খালি-পায়ের এক মুণ্ডা বৃদ্ধ যেন আকাশ থেকে হঠাৎ-ই পথে পড়ে আমাদের পথজুড়ে দাঁড়িয়ে ডানহাতটি ওপরে তুললেন।
কিছুক্ষণ স্তব্ধতা।
তারপরই মুণ্ডারি ভাষায় আমাদের বললেন, দাঁড়াও!
গুরবা খুবই ঘাবড়ে গেল মনে হল।
অস্ফুটে, ভয়ার্ত গলায় বলল, বাঙালিবাবু!
ওর ভাবগতিক দেখে মনে হল নিরস্ত্র অবস্থায় বড়ো বাঘের সামনে পড়লেও ও এত ঘাবড়াত না।
কিন্তু সেই ভৌতিক মানুষটির মুখে রাগ ছিল না।
মুণ্ডারি ভাষায় দু-একটা শব্দই আমি জানি কিন্তু কথাবার্তা চালাবার মতো ভালো জানি না। তাই গুরবাকে বললাম, জিজ্ঞেস কর তো এগিয়ে গিয়ে উনি কেন আমাদের রাস্তা আটকালেন?
গুরবা ওঁর কাছে গিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে মুণ্ডারি ভাষাতে কী সব বলল। কিন্তু বুঝলাম শুধু শেষের বাক্যটিই : বাঙালিবাবু?
বাঙালিবাবু পরিষ্কার বাংলায় খুবই বিস্মিত হয়ে বললেন, আপনারা বাঙালি?
শুভেন থতমত খেয়ে বললে, হ্যাঁ।
ছি! ছি :! শিক্ষিত লোক হয়ে আপনারা শিকার করেন? কোন অধিকারে বনের পশু পাখি মারেন আপনারা?
জ্যোতি একটু উদ্ধত প্রকৃতির এবং খর-মেজাজের মানুষ। সে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টকেই জিজ্ঞাসা করবেন।
বাঙালিবাবু জ্যোতির কথার উত্তর না দিয়ে আমাকে বললেন, আপনারা এই তিনজনই এসেছেন?
জ্যোতি কথা কেড়ে বলল, হঠাৎ এই প্রশ্ন? তিনজনই কি যথেষ্ট নই?
আমি তাড়াতাড়ি বললাম, না, না, আমাদের আর এক বন্ধু ম্যাকলাকসিও আছে। সে। স্কটসম্যান। কাল রাতে মাচা থেকে নামবার সময় পায়ে চোট পাওয়াতে আজ আসতে পরেনি। বাংলোতেই আছে।
জ্যোতি বলল, রোদে ইজিচেয়ার পেতে ঠ্যাং তুলে নভেল পড়েছে সারাদিন।
জ্যোতির তাচ্ছিল্যকে সম্পূর্ণ তাচ্ছিল্য করেই উনি বললেন, সঙ্গে সাহেবও আছে? তবে তো আর কথাই নেই। আপনাদের আর ছোঁয় কে? সাহেবি আমলেও সাহেবদের এত প্রতিপত্তি ছিল না এই দেশে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এখন যেমন হয়েছে। বাঙালির মতো এমন সাহেব-চাটা জাতও তো আর নেই! এত বছরেও ইনফিরিয়োরিটি কমপ্লেক্স কাটাতে পারল না তারা।
জ্যোতি বলল, অন্ধকার হয়ে আসছে, আমাদের তাড়া আছে, এখুনি না নামলে সময়মতো বাংলোয় পৌঁছোতে পারব না। সঙ্গে একটা টর্চও নেই। রাত হয়ে যাবে যে, তা তো ভাবিনি।
কোন বাংলোয় উঠেছ? এখানে তো বাংলো আছে দুটি।
বৃদ্ধ তুমি করে বলাতে জ্যোতির বোধ হয় আত্মাভিমানে লাগল। রাগের গলায় বলল, শালডুংরি।
ও।
তারপর স্বগতোক্তির মতোই বললেন, অনেকদিন বাংলায় কথা বলিনি শিক্ষিত মানুষের সঙ্গে।
তারপরই বললেন আবার, কতদিন থাকা হবে?
জ্যোতিই কথা বলছিল আমাদের হয়ে। ও বলল, আমরা পরশুদিনই চলে যাব।
তারপর আমাকে দেখিয়ে বলল, আমাদের বন্ধু সত্যেন থাকবে আরও দশ দিন। একাই। ওর একটু লেখা-টেখার বাতিক আছে তো। রাইটিং-বাগ-এ কামড়ায়নি এমন বাঙালি তো কমই! আসলে এই কাব্যি-রোগেই খেল তো জাতটাকে!
তাই-ই বা: বাঃ। তাহলে তো তোমার সঙ্গে দেখা হয়েই যাবে একদিন না একদিন টিগেরিয়া অথবা চাঞ্ছোলার হাটে। তখনই কথা হবে এখন। তবে শিকার করা ছেড়ে দাও। আমি একসময় অনেক শিকার করেছি। কিন্তু বড়োই অপরাধবোধ করি এখন। তা ছাড়া পাপও লাগে। পাপ যে লাগে, তা এখন বুঝবে না, পরে বুঝবে।
জ্যোতি বলল, ভেবে দেখব আপনার কথা। এখন চলি।
বলেই গুরবাকে সামনে ঠেলে দিয়ে নিজেও এগিয়ে গিয়ে পাকদন্ডী দিয়ে নামতে লাগল।
আমার খুবই খারাপ লাগল। শত হলেও, বৃদ্ধ মানুষ। এবং আর যাই হোক মানুষটি নিশ্চয়ই খুব ইন্টারেস্টিং। নাহলে আমাদেরই মতো যৌবনে একদিন শিকার করতে এসে এইরকম জঙ্গলে জংলি মেয়ে বিয়ে করে নিজেও জংলি হয়ে গিয়ে এমন করে থেকে যেতে পারতেন না। অসাধারণ কোনো প্রকৃতি এবং দৃঢ়তাও তাঁর মধ্যে না থাকলে এই ব্যাপার সম্ভবই হত না। আসাধারণত্ব মানেই বিরাটত্ব নয়। বা মহত্ত্বও নয়। সাধারণ্য-র ব্যতিক্রম হলেই তা হয় আসাধারণ। এইসব মানুষ সম্বন্ধে জানতে ছেলেবেলা থেকেই আমার প্রচন্ড উৎসাহ ছিল। ব্যতিক্রমী মানুষ তো বেশি নেই। ক্রমশই তাদের সংখ্যা কমে আসছে। জ্যোতির ওপর এজন্যে খুবই রাগ হল। যে তরুণরা তারুণ্যর গর্বে বার্ধক্যকে অপমান করে তাদের যা-ই হোক শিক্ষিত বলে আমি অন্তত মানতে রাজি নই।
ওরা সবাই এগিয়ে গিয়েছিল। ওদের দিকে যেতে বৃদ্ধকে বললাম, কিছুটা জ্যোতির দোষ ক্ষালনের জন্যও; আমি আপনার কাছে আসব একদিন।
আমি কোথায় থাকি তুমি কি জানো?
উনি আমার দিকে মুখ ঘুরিয়ে বললেন।
গুরবাকে নিয়ে আসব। ও নিশ্চয়ই জানে।
হ্যাঁ, গুরবা তো জানেই। এসো। তুমি লেখক শুনে খুবই ভালো লাগল। আমিও লেখক ছিলাম একদিন। তবে আমার লেখা কোথাও ছাপা হয়নি।
তখন আর কথা বলার সময় ছিল না। দ্রুত অন্ধকার নেমে আসছিল। টুপি না থাকায় মনে হচ্ছিল মাথার ওপর কেউ যেন বরফের চাঁই বসিয়ে দিয়েছে। রাইফেলটা দু-কাঁধের ওপর ফেলে দু-হাতে সেটা লাঠির মতো ধরে বড়ো বড়ো পা ফেলে আমি জ্যোতিদের অনুসরণ করলাম। অন্য কিছুই বলার সময় ছিল না। কোনো বিদায়-সম্ভাষণও নয়। অন্ধকারের মধ্যে অন্ধকার যেমন মিশে যায় তেমন করেই বৃদ্ধ মিশে গেলেন অন্ধকারে। আমি দ্রুত নামতে লাগলাম শীতসন্ধ্যার পথপাশের পুটুসের ঝাড়ের তীব্র-কটুগন্ধি পাকদন্ডী বেয়ে।
.
০২.
যে বড়ো মদ্দা বাঘটি মারার জন্যে আমরা গত সাতদিন অনেকই চেষ্টা করলাম, মাচায় বসে, জিপে ঘুরে, হাঁকোয়া করে সেই বাঘ মারতে পারা তো দূরস্থান, তাকে একবার চোখের দেখাও দেখা হল না। আমাদের সকলেরই মন খারাপ ছিল সেই কারণে।
গুরবা বলেছিল, এই বাঘের নাম চাঁন্দা-রাজা। একে যদি কেউ মারতে পারে তাকে চাঁদেরই বরপুত্র হতে হবে। এর জান নাকি নরম হয়ে আসে শুধুমাত্র পূর্ণিমার রাতেই। সেইরকম কোনো উজলা রাতে একে কায়দা করতে পারলে তবেই সে শিকারি চাঁন্দা-রাজাকে। পাবার দুর্লভ সম্মান অর্জন করতে পারে।
বনে-জঙ্গলে থাকতে থাকতে মানুষদের মনে কতরকমের সু এবং কুসংস্কারই যে জন্মে যায়।
শুনেছিলাম, মায়ের কাছে যে, আমার জন্মস্থানে চন্দ্র আছে। কিন্তু কেন যেন আমার সেই চাঁন্দা-রাজার প্রতি আর কোনো ঔৎসুক্যই রইল না। আজ লাঞ্চের পরেই ছিপ নিয়ে ওরা সকলেই চলে যাবে। ট্রেন ধরবে রায়পুর থেকে।
অথচ সেই বৃদ্ধ বাঙালিবাবুর সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকেই কেন যেন চাঁন্দা-রাজার ওপর আমার আর কোনো আকর্ষণই আর নেই। মনের মধ্যে চাঁন্দা-রাজার জায়গা কেড়ে নিয়েছেন সেই বৃদ্ধ। মন কেবলই বলছে, এই বুড়োর মধ্যে অনেক গল্প, অনেক রহস্য জড়িয়ে আছে। মধ্যপ্রদেশের এই জঙ্গলে এ জীবনে আর কখনো আসব কি না তারও কোনো ঠিক নেই। চাঁন্দা-রাজা অথবা সূর্য-রাজা আরও অনেক জঙ্গলেও পাওয়া যেতে পারে কিন্তু এই মানুষটির রহস্য ভেদ এখানে না করে গেলে আর কখনো করা হয়ে উঠবে না।
কাল বিকেলে ম্যাকলাকসি আর শুভেন যখন চাঁন্দা-রাজারই আশায় মাচায় বসতে যাচ্ছিল জিপে করে, পথে নাকি ওই বাঙালিবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল ওদের। উনি হাট করে ফিরছিলেন। কথাও হয়েছে তাঁর ওদের সঙ্গে। ম্যাকলাকসি তো এখনও উত্তেজিতই হয়ে রয়েছে। চাঁন্দা-রাজার সঙ্গে দেখা হলেও বোধ হয় সে এতখানি উত্তেজিত হত না। ও এবং শুভেন যা বলল, তা সত্যিই অত্যন্ত আশ্চর্যজনক। সেই বাঙালিবাবু নাকি স্কটল্যাণ্ডের ম্যাকলাকসিকে হ্যাগেস-এর গান পর্যন্ত শুনিয়ে দিয়েছেন। সে বুড়ো নাকি ইংল্যাণ্ডে তো বটেই, স্কটল্যাণ্ডেও বেশ কিছুদিন ছিলেন। ওঁর যৌবনে। সেই সময়ের খুব কম ভারতীয়ই ইংল্যাণ্ডে পড়াশোনা করতেন বা স্কটল্যাণ্ড দেখেছিলেন। পেশায় নাকি ছিলেন পদার্থবিদ। ট্রম্বের অ্যাটমিক এনার্জি কমিশনের গোড়াপত্তনের ব্যাপারে জওহরলাল নেহরু নাকি হোমি ভাবা সাহেবের ওপর সমস্ত দায়িত্ব দেওয়ার আগে এই বাঙালিবাবুকেই অনুরোধ করেছিলেন ভারতের অ্যাটমিক এনার্জি কমিশনের ভার নেওয়ার জন্যে।
আমার কিন্তু বিশ্বাস হল না শুনে। যে মানুষ প্রথম আলাপেই নিজের সম্বন্ধে এত কথা বলেন, সে মানুষ সম্ভবত জাল। দু-নম্বর। আজকালকার অধিকাংশ শিক্ষিতদের মতো। যাদের শিক্ষা শুধু অক্ষর পরিচয়েই এসে থেমে গেছে।
ম্যাকলাকসি বলল, এত সুন্দর অকসনিয়ান অ্যাকসেন্টের ইংরিজি সে খুব কম ভারতীয়র মুখেই শুনেছে। আমাদের সকলের ইংরেজিতেই নাকি দেশজ টানটুন থাকেই। যা আমাদের কানে লাগে না, ওদের কানে ঠিকই ধরা পড়ে।
শুভেনও যেন মত পালটেছে। বলছিল, এ বড়ো রহস্যময় বুড়ো। রোদ-বৃষ্টিতে পোড়া চেহারার সেই বৃদ্ধ যে গুরবার বাবা কি জ্যাঠা নয় এই কথা বিশ্বাসও করা যায় না। পায়ে জুতো নেই, পরনে হাঁটুর ওপর তোলা মোটা ধুতি আর হাট থেকে কেনা ছিটের জামা, বোতামবিহীন। এলমেলো সাদা চুল-দাড়ি। এই বুড়ো হয় পাগল, নয় শয়তান।
লাঞ্চের পর ওরা সকলেই চলে গেল। ওদের রায়পুর স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে ড্রাইভার যুগলপ্রসাদ আবার জিপ নিয়ে ফিরে আসবে।
আমার হাতে একটা বড়ো লেখা ছিল। সম্পাদকের সনির্বন্ধ অনুরোধে তা শেষ করে নিয়ে যেতে হবে কলকাতায় ফেরার আগে। এখান থেকে ফিরেই জমা দিতে হবে দপ্তরে। কলকাতায় ওদের সঙ্গে ফিরে গেলে লেখাটা শেষ করতে অনেক বেগ পেতে হত। কলকাতায় শান্তিতে, বিনা উপদ্রবে কিছু করারই জো নেই। তাই-ই থেকে যাওয়া। আমার ছুটিও শেষ হতে বাকি ছিল এখনও দু-সপ্তাহ। থাকতে তাই অসুবিধেও ছিল না কোনো।
বিকেলবেলায় বাংলোর বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে, চেয়ারের দুটো লম্বা হাতলে দু-পা তুলে দিয়ে সাতপুরা পর্বতমালার উঁচু এবড়ো-খেবড়ো পাঁচিল যেখানে মেঘের সঙ্গে গিয়ে মিশেছে সেদিকে চেয়ে থাকতে থাকতে অন্যমনস্ক হয়ে গেছিলাম। একটা ক্রেস্টেড-ইগল ঘুরে ঘুরে চক্রাকারে সেই পাহাড় ছাড়িয়ে শীতের বিকেলের নির্মেঘ আকাশের নীল চাঁদোয়া কুঁড়ে যেন কোনো অন্য গ্রহের দিকে উড়ে যাওয়ার চক্রান্ত করছিল। বাংলোর চারপাশ থেকে তিতির ডাকছিল র্চিহা-চিঁহা-চিহা করে। বাংলোর হাতার সামনের কাঁটাতারের পাশে ঘন হয়ে গজিয়ে-ওঠা ল্যান্টানা ঝোঁপের নীচে নীচে সেভেন-সিস্টারস পাখিরা নড়েচড়ে, সরে সরে তাদের কর্কশ ডাক ডেকে পরিবেশের নিথর নিস্তব্ধতাকে বারে বারে চমকে দিচ্ছিল। চৌকিদারের বউ কুয়ো থেকে জল তুলছিল। লাটাখাম্বার আওয়াজ উঠছিল ক্যাঁচোর-কোঁচর।
বাংলোর পেছনে শালডুংরি বস্তি থেকে কোনো মা তার দুখিয়া নামের শিশুসন্তানকে দূর উপত্যকার দিকে চেয়ে বারে বারে মুখ তুলে ডাকছিল। বোধ হয় সে ছাগল চরাতে গেছে, বনের গভীরে।
বাংলোর বারান্দার সামনে রোজই ক্যাম্প-ফায়ার হয়েছে সন্ধের পর এই ক-দিন। সেখানে ময়ূরের বারবিকিউ, কুটরা হরিণের কাবাব এইসব বানিয়েছে শুভেন। আজ কাঠ কিছু কম পড়ে গেছে। এতদিন বাজে-পুড়ে যাওয়া একটা মস্ত হলুদ গাছের গুঁড়ি আমাদের উত্তাপ জুগিয়েছে। সেও আজ সকালে সম্পূর্ণ ভস্মীভূত।
চৌকিদার পেছনের জঙ্গলে মরা গাছের ডাল কাটতে গেছে রাতের আগুনের জন্যে। তার টাঙ্গির কোপের খটাখট আওয়াজ বাংলোর প্রাচীন দেওয়ালে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে যাচ্ছে আবার তারই দিকে। বুমেরাং-এর মতো।
একটু পরেই রোদ পড়ে যাবে। উষ্ণতা মরে গিয়ে ঝুপ করে শীতার্ত অন্ধকার নেমে আসবে অদৃশ্য অতিকায় বাদুড়ের মতো আদিগন্ত ডানা মেলে। বনপথের দু-পাশের লাল ধুলো-মাখা গাছগাছালি, ঝোঁপঝাড় এক বিনি-পয়সার মৃত্তিকাগন্ধি আতরে গন্ধবতী হবে। এইরকম রাতে, এইরকম বাংলোর বারান্দায় বসে আগুনের ফুটফাট স্বগতোক্তির মধ্যে সেই বাঙালিবাবুর মতো কোনো মানুষের জীবনের অভিজ্ঞতার কথা শুনতে বড়োই সাধ যায় আমার।
কাল সকালে লেখালেখি সেরে, চান করে নিয়ে নাস্তা খেয়ে গুরবারকে নিয়ে আমি যাবই তাঁর কাছে।
বলেও রেখেছি গুরবাকে।
.
০৩.
বাড়িটা অতিসাধারণ, সামান্য। যেমন আর দশজন মুণ্ডাদের বাড়ি হয়। তফাত এইটুকুই যে, বাড়ির চারপাশে শৌখিন গাছগাছালি, যা এই বন-পাহাড়ের জংলি গাছপালা নয়, তাও অনেক আছে। বড়ড়াও হয়েছে বেশ তারা। অনেকদিন আগে লাগানো জ্যাকারাণ্ডা, আকাশমণি বা আফ্রিকান টিউলিপ, কেসিয়া নস্যুলাস, সোনাঝুরি, অমলতাস, দুটি ইউক্যালিপটাস, একটি সজনে গাছ, একটি কনকচাঁপা, এবং দুটি কদম। কদম অবশ্য এই জঙ্গলেই হয়। জঙ্গলে বেলও হয়।
তবে এরা মানুষের হাতে সযত্ন-বর্ধিত। জঙ্গলের নয়। এককালে যেখানে একটি তোরণের মতো করা ছিল বোগেনভেলিয়া এবং বুনো জুইরের লতা দিয়ে, যে তোরণের নীচ দিয়ে বাড়ির উঠোনে ঢুকতে হত, এখন তা অনেকটাই বিস্রস্ত, এলমেলো।
উঠোন মধ্যিখানে। তিনটি ঘর তিন পাশে। ঘরগুলির মাটির দেওয়ালে বনজ রং দিয়ে আঁকিবুকি করা। রং এখন ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।
লক্ষ্মী শুধুমাত্র কুলুঙ্গির মধ্যেই থাকেন না। যে বাড়ির লক্ষ্মী চলে যায় সে বাড়ির সামগ্রিক চেহারাতেও তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ বাড়িরও তেমনই! গেট দিয়ে ঢুকতেই মনে হল এই বাড়ি কোনো লক্ষ্মী নারীর পরশ পেয়েছিল একসময়। সেই নারীই ছিল লক্ষ্মীর দূতী। নারীহীন বাড়িতে লক্ষ্মী যদি থেকেও যায় তবুও সে বাড়িকে বড়োই হতশ্রী ঠেকে চোখে।
উঠোনে দাঁড়িয়েই গুরবা ডাক ছাড়ল বাঙালি বাবু বলে।
ডানদিকের ঘর থেকে একজন সদ্য যুবক বেরিয়ে এল।
তার পরনে লাল রঙের ব্যাংলনের গেঞ্জি নীচে জিনের ট্রাউজার, পায়ে টায়ারসোলের চটি। মাথায় বাবরি চুলের শেষপ্রান্তে গেঁথে রাখা ক্যাটকেটে হলুদ-রঙা প্লাস্টিকের একটি কাঁকই। তার হাবভাব বেশ উদ্ধত। দেখে মনে হল, বয়েসে আমার চেয়ে সে অনেকটাই ছোটো হবে। তবে আদিবাসীদের সুস্বাস্থ্যের কারণে তাদের প্রায়ই বয়সের চেয়ে কমবয়েসি মনে হয়। ছেলেটি কৈফিয়ত চাইবার গলায় গুরবাকে কী যেন বলল, ওদেরই ভাষায়। আমরা আসাতে সে যে খুশি হয়নি তা স্পষ্টই বুঝিয়ে দিল চোখের ভঙ্গিতে এবং ঠিক সেই সময়ই ঘর থেকে সেই বৃদ্ধ বেরিয়ে এলেন। গুরবার বাঙালিবাবু হাতজোড় করে বাঙালি কায়দায় বললেন, নমস্কার! নমস্কার! এসো ভাই এসো। উঠোনেই বসি। কী এল? রোদ তো এখন মিষ্টিই লাগে। এই রোদ আর হাওয়া আর জল ছাড়া আর তো কিছুই নেই আমাদের এখানে। কিন্তু পনেরো দিন থাকো, কলকাতায় আর ফিরতেই ইচ্ছা করবে না।
বলেই, দুটি শালকাঠের তক্তার ওপরে পেরেক-মেরে বানানো একটি টুল ঘরের ভেতর থেকে টেনে এনে আমাকে বসতে দিলেন।
ঠিক সেই সময়ই সেই যুবক উদ্ধত ভঙ্গিতে বৃদ্ধকে কী যেন বলল।
বৃদ্ধ ওদিকে মুখ পর্যন্ত না ফিরিয়ে উত্তেজনাহীন নির্বিকার গলায় জবাব দিলেন।
নিরুত্তরে সেই উদ্ধত যুবক চলে গেল গেট পেরিয়ে গ্রামের দিকে। একটু পরই তার লাল রঙা ব্যাংলনের গেঞ্জি হারিয়ে গেল শীতের ধূলিমলিন সবুজ হিজিবিজি জঙ্গলের গভীরে।
বৃদ্ধ বললেন, ভেবেছিলাম আজ চাঞ্ছোলার হাটেই দেখা হয়ে যাবে তোমার সঙ্গে বিকেলে। তা না, ভালোই হল, তুমি নিজেই এলে বাড়ি বয়ে।
আমি এরপর ওঁকে নিয়ে পড়লাম। যে কারণে আসা। আমার উৎসুক প্রশ্নের পর প্রশ্নের উত্তরে বৃদ্ধ যা বললেন ধীরে ধীরে, তাতে আমার মন ভরল না। ভেবেছিলাম, শহরের লেখাপড়া-জানা সচ্ছল মানুষ আমি, আমার এই জংলি, গরিব, অসহায়, একাকী বৃদ্ধের প্রতি এই অস্বাভাবিক ঔৎসুক্য ওঁকে গর্বিতই করবে। কিন্তু মনে হল ঔৎসুক্য নামক অনুভূতিটি এই বৃদ্ধের মস্তিষ্ক ছেড়ে চলে গেছে বহু বছর হল।
বৃদ্ধ বললেন, খুব নীচুস্বরে : এই পৃথিবীতে বড়ো বেশি কথা হয়। তাই না? যার নিরানব্বই ভাগইবলা না হলেও মানুষের কোনোই ক্ষতি ছিল না। বয়েসও হয়েছে বিরাশি। অনেকই অপ্রয়োজনীয় অবান্তর কথা বলেছি এই একজীবনে। এত বাজেকথা বলার জন্যে নিজেকে এখন সব সময়ই ধিক্কার দিই। বলেছি বেশি; শুনেছি কম। তাই যে কটা দিন বাকি আছে; সে কটা দিন একটু ভাবতে চাই। শুনতে চাই। মানুষের মনের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম; এই জঙ্গলের, পাহাড়ের, ঘনান্ধকার রাতের কী বলার আছে সেইসব। তুমি তো শিকারি সত্যেন। এদের কথা কখনো কি শুনতে চেয়েছ? বনে-জঙ্গলে তো ঘুরলে অনেকই তুমি?
আমি জবাব না দিয়ে চুপ করে রইলাম।
বৃদ্ধ নিজের ঘরে গেলেন, ফিরে এলেন হাতে একটা মলিন, ছিন্ন, মোটা অ্যালবাম নিয়ে। অ্যালবামটি আমার হাতে দিয়ে বললেন, চা খাবে তো?
তারপর আমার জবাবরে অপেক্ষা না রেখেই বললেন, আমি তিরিশ বছর আগে চা খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি। তবে তুমি আসতে পারো ভেবে, কালই বিকেলে বস্তি থেকে একটু চা এনে রেখেছিলাম। তুমি বোসো, আমি চা করে আনছি তোমার জন্যে। অবশ্য নামেই চা। গরম জলেরই নামান্তর।
আমাকে আপত্তি করার কোন সুযোগ না দিয়েই সেই বৃদ্ধ নিজের ঘরের দিকে চলে গেলেন। বুঝলাম, ঘরেরই মধ্যে একপাশে রান্না-বান্না করেন।
ফিরে এসে, নিজে ঘরের দাওয়াতে বসে, মুখটি জঙ্গলের দিকে ফিরিয়ে বললেন, ছবিরা কথা বলে, জানো!
কথাটা আমাকেই বললেন, না জঙ্গলকেই, তা বোঝা গেল না।
আবারও বললেন, এ অ্যালবামে তোমার অনেক প্রশ্নেরই উত্তর ছবি হয়ে ফুটে আছে। এরপরও যদি কিছু জিজ্ঞাস্য থাকে তাহলে শুধু সেটুকুই শুধিয়া।
বৃদ্ধ, আমাকে এবং বোধ হয় জঙ্গলকেও একইসঙ্গে বললেন আবার।
অ্যালবামের প্রথম পাতাটি খুলেই আমি একেবারেই চমকে গেলাম। একজন পুরোদস্তুর সাহেবি মানুষ ব্রিচেস-পরা। পায়ে যোধপুরি শিকারের বুট। ওপরে শুটিং-জ্যাকেট, জ্যাকেটের বুকের দু-দিকে রাইফেলের গুলি রাখার খাঁজ-কাটা পকেট। মাথায় অলিভ-গ্রিন রঙের গরম কাপড়ের বেরে ক্যাপ। মুখে পাইপ। সেই পাইপের কাঠের মসৃণতা ফোটোতে এখনও উজ্জ্বল। খুব উচ্চ-বর্ণের পাইপ। মনে হল, ডানহিল। কাঁধে, ঝকঝকে নীলাভ-কালো রং-করা ব্যারেলের রাইফেল। অস্ট্রিয়ান, ইংলিশ বা জার্মান। দীর্ঘদেহী, সুগঠিত সাহেব সুপুরুষ।
ছবিগুলির মধ্যে একটি ছবি বোধ হয় গরমের সময় ভোলা। খাকি শর্টস পরা, পায়ে পাতলা রাবার সোলের শিকার-করার জুতো, গায়ে সাফারি-শার্ট, হাতে ডাবল-ব্যারেল, হেভি-বোরের রাইফেল। পায়ের কাছে একজোড়া কেঁদোবাঘ মরে পড়ে আছে। জঙ্গলেরই ভেতরে তোলা ছবি।
অ্যালবামের পরের পাতাটি জুড়ে একজন অসামান্য জংলি রূপসি। নিমফুল আর করৌঞ্জের তেল-মাখা মসৃণ-মুখের দীর্ঘদেহী সুতনুকার; এক মুণ্ডা যুবতীর ছবি। তাঁর দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গি তো নয়; যেন বসন্ত বেজেছে নবীনা অমলতাস গাছে। তারপরের পাতাতেই তাঁরই, প্রায়-বিবস্ত্র ছবি। গ্রীষ্মের শুকিয়ে যাওয়া সাদা বালির নদীরেখার বুকে পত্রহীন জঙ্গলের পটভূমিতে দাঁড়ানো। কটিদেশে ফুলের ঝালর। উন্মুক্ত, উদবেল স্তনদ্বয়। মুখে, পবিত্র বনমালার স্নিগ্ধ বৈশাখী ভোরের মতো হাসি ছাড়া আর কোনোই প্রসাধন নেই। আর তারপরের পাতাতে এই বাড়িটিরই একটি ছবি।
বাড়িটি তখন আরও অনেকই সুন্দর ছিল।
তারও পরের পাতায় উঠোনে হামাগুড়ি-দেওয়া একটি উলঙ্গ শিশুর ছবি তোলা হয়েছে বিভিন্ন ভঙ্গিমায়। আরও পরে, অ্যালবামের প্রায় শেষে বৃদ্ধের যৌবনকালের ছবি কিন্তু তিনি তখন দ্বিজ। জনমে দ্বিজ নয়; জীবনে দ্বিজ। খালি পা, খালি গা; কোমরে মালকোঁচা-মারা মোটা-ধুতি পরে কাঠের বোঝা মাথায় নিয়ে যাচ্ছেন।
আরও পরে অ্যালবামের শেষের দিকে সেই যুবক-যুবতীরা যখন প্রৌঢ়ত্বের দরজায় এসে পৌঁছেছেন, তখনকার দিনের কিছু ছবি। শিশু তখন কিশোর।
তারপরে আর কোনোই ছবি নেই। সব পাতাই ফাঁকা।
আমার মনও ফাঁকা হয়ে গেল। বৃদ্ধর প্রতি, কেন জানি না, এক ধরনের শ্রদ্ধামিশ্রিত গভীর বিস্ময় জন্মাল।
গ্লাসে করে চা নিয়ে উনি বাইরে এলেন। চায়ের গ্লাস হাতে নিয়ে আমি গুরবাকে বললাম, আর একটা গ্লাস আনো, তোমাকে চা দিই।
উনি বললেন, না, না, না, তুমি দেবে কেন? আমাদেরও বানিয়েছি। আস্ত গ্লাস একটাই ছিল, তাই আগে এনে দিলাম অতিথিকে। আমরা জংলি লোক, তাই ফুটোফাটা গ্লাসেই চলে যাবে আমাদের।
ঘরে গিয়ে দুটো অতিকম দামি, ফাটা এবং নীলাভ কাঁচের গ্লাস এনে একটা গুরবাকে দিয়ে এবং একটা নিজে নিয়ে তাঁর ঘরের দাওয়ার খুঁটিতে আবারও হেলান দিয়ে বসে পা দুটো বুকের কাছে জড়ো করে বৃদ্ধ চায়ের গ্লাসে চুমুক দিয়ে বললেন, আ-হঃ! অনেক বছর পরে চা খেলাম। বুঝলে সত্যেন!
শব্দ করে চা-খাওয়া সাহেবি কেতায় বেজায় অসভ্যতা। এককালের পুরোদস্তুর সাহেব এই বৃদ্ধ যে পুরোপুরিই জংলি হয়ে উঠেছেন তাতে সন্দেহ রইল না কোনোই।
আমি গ্লাসে চুমুক দিয়ে বললাম, চা তো খেলেই পারেন। বৃদ্ধ হাসিমুখে বললেন, অপ্রয়োজনীয় বিলাস আর কিছু রাখিনি এখন। তবে যা কিছুই আমি একদিন ছেড়ে দিয়েছিলাম একে একে; আমার ইংরিজি জানার গর্ব, সাহেবি পোশাক, নানা নেশার বিলাসিতা সবই ফিরে আসছে আমার একমাত্র বংশধরের মধ্যে। যদিও ও শিক্ষার আলোর মুখ পর্যন্ত দেখেনি এবং দেখবে বলে মনে হয় না। তবু এই ফালতু ইংরিজিআনার অনুষঙ্গ ওর মধ্যে পুরোপুরি সোচ্চার এবং প্রবল দেখতে পাই।
অনুষঙ্গ ও সোচ্চার শব্দ দুটিতে চমকে উঠলাম আমি। বৃদ্ধ যে বাংলা ভালোই জানেন সে বিষয়ে সন্দেহ রইল না। সাধারণ বাংলা-জানা লোকে এইসব শব্দ ব্যবহার করেন না।
অন্যমনস্ক গলায় বৃদ্ধ বললেন, আমার জীবনটা বৃথাই হয়ে গেল। যে-বিশ্বাসে ভর করে আমার সব প্রাপ্তিকেই তথাকথিত অপ্রাপ্তিতে পর্যবসিত করেছিলাম সেইসব অপ্রাপ্তিরই কামড়ে আমার একমাত্র সন্তানের শরীর-মন বুঝি জ্বলে-পুড়ে যাচ্ছে। আমি একসময়ে যা ছিলাম, তার সবটুকু বিলীন করেই অন্য-আমি হয়ে উঠেছিলাম, অথচ আমার ছেলে আমার ফেলে-দেওয়া পোশাকেরই মতো সেই ছুঁড়ে দেওয়া জীবনকেই অনেক বেশি দামি বলে মনে করল।
আমি চুপ করে রইলাম বৃদ্ধের মুখে দিকে চেয়ে।
পরে শুধোলাম, কেন?
নীচুগলায় উনি বললেন, আমি হেরে গেছি ভাই। হেরে গেছি নিজের রক্তের কাছে; আত্মজের কাছে। এখন আমার বাঁচা-মরা দুই-ই সমান।
আপনি যা বলতে চাইছেন তার পুরোটা না হলেও হয়তো তার কিছুটা বুঝেছি। কিন্তু আপনিই বা এত অভিমানী কেন? ওদের, মানে, এই নতুন প্রজন্মকে একটু বুঝিয়ে বললেই তো পারেন। অভিমান করে থেকে লাভ কী?
অভিমান?
শব্দটা উচ্চারণ করেই বৃদ্ধ হেসে ফেললেন।
বড়োই করুণ সে হাসি।
বললেন, অভিমান শব্দটা আজ অচল হয়ে গেছে। আজকের মানুষদের অভিধানে অভিমান বলে কোনো শব্দ আর নেই। অভিমান তো অন্তর্জগতেরই ব্যাপার। এদের অন্তর্জগৎ কিছু নেই। অন্তর্মুখীনতা শব্দটাকেও ওরা ভয় পায়।
কথা কেটে আমি বললাম, এটা বোধ হয় আপনি বেশি বলছেন। অন্তর্জগৎ ছাড়া কি মানুষ হয়? অন্তর্জগতের স্বরূপ, সে তত যুগে যুগে পালটে যায়ই। এই-ই যা। আগেও পালটেছে, ভবিষ্যতেও পালটাবে।
বৃদ্ধ যেন নিজের মনেই বললেন, আমি তো অতিসামান্য একজন মানুষ। আমি একা। আমার ভাবনাও আমার একার। আমার জীবন-দর্শন বাতিল হয়ে গেছে। তা ছাড়া এখন সেনাইলই হয়ে গেছি হয়তো। আমার জ্ঞানও তামাদি হয়ে গেছে। আমার সাধ্য কী যে আমি ওদের বা তোমাদের বাঁচাই? বোঝাই? যারা মরবে বলে পণ করেছে, তাদের বাঁচানো যে বড়ই কঠিন।
চায়ের গ্লাস নামিয়ে রেখে বললাম, আমি কিন্তু এই কথা মানি না। আপনি বাবা, যদি বুঝিয়ে ছেলেকে বলেন; ছেলে বুঝবে না? আপনার ওই বয়েসে যে বুদ্ধি ছিল তার চেয়ে ওদের বুদ্ধি যে অনেকই বেশি, এই কথা কি আপনি অস্বীকার করেন?
বৃদ্ধ আবারও হেসে বললেন, বলেইছি তো। অনেক বেশি কথা বলা হয়ে গেছে। যে-কথা অন্যে শোনে না, শুনতে চায় না; সেই কথা বলে নিজেকে এই বয়েসে আর ছোটো করা কেন?
না না, আপনি বলুন, আমি শুনব।
বৃদ্ধ হেসে বললেন, তুমি শুনবে সত্যেন? জানো তুমি; আমি-না, কুয়াশা হয়ে গেছি। জানো, কুয়াশারই মতো আমি সিক্ত, বিস্তৃত, অস্পষ্ট হয়ে গেছি। তোমরা যেমন আমার মধ্যে অন্য আমিকে দেখতে পাও না, তেমনি আমিও পাই না তোমাদের অন্য সত্তাকে দেখতে।
আমি চুপ করে রইলাম। কোনো মানুষ যে নিজেকে কুয়াশার সঙ্গে তুলনা করতে পারেন এমন উপমার কথা ভাবিনি।
উনি বললেন, তোমাদের প্রজন্ম হচ্ছে বিদ্যুতের প্রজন্ম। তোমরা অনেকই বোঝো। তোমরা দপ করে জ্বলে উঠে ঝুপ করে নিভে যাও। জানো সত্যেন, আমার অনেক কিছুই বলার ছিল; ছিল অনেক কিছু করারও। কিন্তু আমি কিছু করিওনি; করবও না কারণ আমার দুটি জীবন। ব্রাহ্মণ না হলেও আমি দ্বিজ। যে-জীবন ছেড়ে এসে আমি এই জীবনে প্রবেশ করেছিলাম সেই পুরোনো জীবন এবং এই নতুন জীবন এই দুই জীবনই আমাকে পুরোপুরি স্থিতপ্রজ্ঞ করে দিয়েছে। আমি স্থির জেনেছি যে, যে-জানা একজন মানুষ নিজের চোখ দিয়ে না জানে, না-জানে তার সমস্ত জীবনের অন্বেষের মধ্যে দিয়ে, সেই জানা-অন্যজন যত বড়ো পন্ডিতই হোন না কেন, তিনি কখনো জানতে পারেন না। আমি কুয়াশা; হ্যাঁ, কুয়াশাই আমি তোমরা বিদ্যুৎ। তোমরা আমাকে বুঝবে না। শতচেষ্টা করলেও না। না, সত্যেন।
আমি ভাবছিলাম, পৃথিবীর সব বৃদ্ধরাই বোধ হয় একইরকম কথা বলেন। কথা বলব না বলে, বড়ো বেশিই কথা বলেন। জ্ঞান দেব না বলে, সব সময়েই জ্ঞান দেন। পৃথিবীর সব শীত তাঁদের লোলচর্ম, ভাঁজ-পড়া ন্যুজ শরীরে এসে বাসা বাঁধে। তাঁদের হাড়ের খোঁদলে খোঁদলে কুয়াশারই মতো জমে যায় শীত। তাঁরা কুয়াশার মতোই অস্পষ্ট। তবে কুয়াশা শব্দটাকে যে এমনভাবে ব্যবহার করা যায়, আমি নিজে একটু লেখালেখি করা সত্ত্বেও কোনোদিনও ভাবিনি। এই বাঙালিবাবুর বাংলা ভাষাতে রীতিমতো অভিনবত্ব আছে!
স্বল্প অভিজ্ঞতাতেও স্থির জানা ছিল যে তর্কে, বৃদ্ধ, নারী এবং কেতাবি-কমিউনিস্টদের সঙ্গে খুব কমই জেতা যায়। তাই প্রসঙ্গ বদলাবার জন্য বললাম, আপনি বলছিলেন না যে, আপনিও লেখালিখি করতেন এক সময়ে?
বোগেনভেলিয়া এবং প্যাশন-ফ্লাওয়ারের তোরণ পেরিয়ে তাঁর চোখদুটি দূর পাহাড়ে নিবদ্ধ করে বললেন, হ্যাঁ বলছিলাম কিন্তু সেই আমিও তামাদি হয়ে গেছি। আমি যা লিখেছি, সেসবকে লেখা বলে না। আমার কথারই মতো, সেই লেখাও তোমাদের মনে আর পোঁছোবে না। পৃথিবী এতই দ্রুত ছুটে চলেছে তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতির দিকে যে, আমার ওই ঢিমেতালের লেখা পড়ার মতো মনও তোমাদের প্রজন্মে কারোরই আর অবশিষ্ট নেই।
একটুক্ষণ চুপ করে থেকে উনি বললেন, জানো সত্যেন! এই পৃথিবী সৃষ্টি হতে লেগেছিল বহুঁকোটি বছর। ভাবলে দুঃখ হয় যে, বিধাতার শ্রেষ্ঠতম জীব মানুষ; যার ওপর ভার ছিল এই পৃথিবীকে ফুল-ফলন্ত, সুখ-ভরন্ত করে রাখার, সেই অহং-সর্বস্ব মানুষই এই পৃথিবীকে কত স্বল্পসময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ প্রলয়ের দিকে প্রচন্ড বেগে টেনে নিয়ে এল। এই ধ্বংসের গতি দুর্বার। একে প্রতিহত করার কোনো উপায়ই নেই। চারদিকে তাকিয়েই একথা বুঝতে পারি। সবকিছুই এখন আওতার বাইরে চলে গেছে; যাচ্ছে।
বলেই, দীর্ঘশ্বাস ফেললেন উনি।
এবারও কথা ঘোরাবার চেষ্টা করলাম আমি। বুড়োমানুষের একই প্যানন্যানানি ভালো লাগছিল না আর।
বললাম, আপনি কী লিখতেন? কোথায় ছাপা হত সেইসব লেখা?
ছাপা তো কোথাও হয়নি। আগেই বলেছি তোমাকে। তা ছাড়া ছাপানোর জন্যে লিখিওনি আমি। যা-কিছুই ছাপা হয় তার সবই কি ছাপার যোগ্য? এই জাল পৃথিবীতে হয়তো উলটোটাই সত্যি!
বৃদ্ধ আবারও হাসলেন। পবিত্র, উদার, কলুষহীন হাসি।
হঠাৎ গুরবা বলল, অনেক দেরি হল, এবার উঠুন সাহেব।
মনে হল ওরও অসহ্য ঠেকছিল বৃদ্ধের এই নিরন্তর বকবকানি। কথা বলার লোক পান না বলেই বৃদ্ধরা কাউকে একবার পেলে ছাড়েন না আর!
আমি লজ্জিত হলাম। বললাম, চলো, এই উঠছি।
ভাবছিলাম, এই বৃদ্ধ হয়তো উন্মাদই। এবং বড়োই বিভ্রান্তিকর। খুবই গোলমেলে। আমার বুকের মধ্যে এতদিন ধরে তিলতিল করে জমিয়ে তোলা সব বিশ্বাস, ভাবনা, ধারণা, সব কিছুকেই তছনছ করে দেওয়ার এক গভীর চক্রান্ত এই মানুষটির মধ্যে আমি লক্ষ করছিলাম। তবু জানি না কেন, এই শীতের রোদের মধ্যে জঙ্গলের গভীরের মাটির বাড়ির বনজ গন্ধ ভরা উঠোনে পেরেক-মারা তক্তার টুলের ওপর বসে এই মানুষটির কথা শুনতে শুনতে আমি যেন বেশ সম্মোহিতও হয়ে গেছিলাম। একঘেয়েমির মধ্যেও এক ধরনের সম্মোহনী শক্তি, ঘুমপাড়ানি ভাব থাকেই! আদিবাসীদের গানেরই মতো।
কুয়াশা!
বেশ কথাটা। মনে মনে বললাম।
তারপর উঠলাম।
বললাম, উঠি আজকে।
বৃদ্ধও মাটির দাওয়া ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমাকে হাতজোড় করে বললেন, আচ্ছা, ভাই, আবারও এসো। আছ ক-দিন?
তারপর উত্তরের অপেক্ষা না করেই বললেন, বহুদিন পর তোমার মতো একজন মানুষের দেখা পেলাম। মানে, একজন প্রাণীর। যাকে আমারই ভাষায় এত কথা বলা গেল। কথা, সব কথা; সকলে বোঝে না। সকলকে সব বলতে যাওয়াটাও মূর্খামি।
তার মানে? আপনি কি এইসব কথা অন্য কাউকেও বলেছেন এর আগে?
নিশ্চয়ই। সব সময়েই তো বলি। তবে মানুষের অবয়বের প্রাণীকে বলিনি কখনো এত কথা। গাছকে বলি, আকাশকে বলি, নদীকে বলি, পাহাড়কে বলি। মুখ আমার বন্ধই থাকে। কিন্তু মানুষের মস্তিষ্ক নিয়ে জন্মেছি তো। সে তো জন্মাবধি, মৃত্যুর ক্ষণ অবধি তার কাজ করেই চলেছে। মানুষের মস্তিষ্ক তো বিশ্রাম কাকে বলে জানে না। ভাবনার ক্ষরণে তো কোনোই বিরাম নেই। যতি নেই নিজের সঙ্গে নিজের কথা বলারও। সত্যি! অন্য মানুষের সঙ্গে নিজের মাতৃভাষায় এত কথা বহু বছর বলিনি। হয়তো তুমি বিরক্ত হলে। বৃদ্ধরা সত্যিই বড়ো বেশি কথা বলে। তবে যদি কখনো টাইম কিল করার প্রয়োজন ঘটে, তখন এই বৃদ্ধর কথাগুলি ভাবতে ভাবতে তোমার সময়কে খুন কোরো।
গুরবা আবারও তাড়া দিল।
বলল, বড়ি দেরি হো গেল সাহাব।
তুম যাতে কাহে নেহি।? ম্যায় ক্যা আওরাত হুঁ, যো জংলি মে খো যায়েগা? তুম আগে বাড়ো, দো পেহরকা খানেপিনেকা ইন্তেজাম করনেকো বোলো চৌকিদারকো, ম্যায় আ রহা হ্যায়।
জি সাব।
বলেই গুরবা বড়ো বড়ো পা ফেলে এবং বোধ হয় হাঁফ ছেড়েও, সেই বোগেনভেলিয়া আর প্যাশন-ফ্লাওয়ারের তোরণের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে জঙ্গলের বাঁকে মুহূর্তের মধ্যে হারিয়ে গেল।
ও চলে যেতেই আমি বৃদ্ধকে বললাম, আপনার কাছে একটি জিনিস চাইতে পারি?
বৃদ্ধ বিস্ময়ভরে আমার দিকে তাকালেন। বললেন, আমি তোমাকে দিতে পারি এমন কী আছে আমার ভাই? বড়ো অবাক করলে!
আপনার সেই ডায়েরির কথা বলেছিলেন। ডায়েরিটা একটু পড়তে দেবেন?
বৃদ্ধ আবারও হাসলেন।
বললেন, পড়তে দেব? শুধু পড়তে কেন? ও জঞ্জাল রেখেই বা কী হবে? তোমাকে একেবারেই দিয়ে দেব। কোনো সম্পত্তির ওপরেই আমার কিছুমাত্র আকর্ষণ নেই। তবে আমার বাংলা হাতের লেখা বড়োই খারাপ। কাটাকুটি, আঁকিবুকি অনেকই আছে তাতে। আমার আঁকা ছবি। চাঞ্জেলার হাট থেকে কত বছর আগে কেনা কাগজ। সেই কাগজও অতিজঘন্য। ফাউন্টেন পেনের কালিও তো ছিল না এখানে। বড়ি-গোলা কালিতে আমার ফাউন্টেনপেনটি ডুবিয়ে ডুবিয়ে লেখা। তা ছাড়া, এত বছরে সেই কালির রং-ও ফিকে হয়ে লালচে হয়ে গেছে। জানি না, পড়তে পারবে কি না আদৌ। একটু দাঁড়াও। আমি নিয়ে আসছি।
যেতে যেতে ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন, তুমি ক-দিন আছ এখানে তা তো বললে না সত্যেন?
আগামী শনিবার সকালে নাস্তা করে জিপেই চলে যাব।
নইলে, জিপটা ফাঁকা যাবে। ড্রাইভারও এতখানি পথ একা।
ও। তবে তো আছই ক-দিন। ডায়েরিটা তোমার পড়া হয়ে গেলে তুমি আমাকে ফেরতও দিয়ে যেতে পারো, যদি মনে করো, তোমার কাছে বোঝা হবে, আর ইচ্ছে করলে, তুমি নিয়েও যেতে পারো। তবে অবশ্য এ কথা ঠিক, আজকে আমি ইচ্ছে করলেও এ ডায়েরিতে যা লিখেছিলাম, তেমন লেখা লিখতে পারব না। তুমি কি থোরোর ওয়াল্ডেন বইটা পড়েছ? থোরো একসময় ওয়াল্ডেন নামের একটা মস্তবড়ো ঝিলের পাশে গভীর জঙ্গলের মধ্যে একেবারেই একা অনেকদিন ছিলেন। তাঁর সেই ডায়েরিটির নামই ওয়াল্ডেন। আমার ডায়েরিও ইংরিজিতে লিখলে এবং বিদেশের কোনো ভালো প্রকাশক পেলে হয়তো ওয়াল্ডেন-এর মতো কোনো পৃথিবীখ্যাত বই হতে পারত। হয়নি যে, সেই কারণে আমার কোনো দুঃখ নেই কারণ আমি এই ডায়েরিতে যা লিখেছি তা আজকের পাঠকদের; মানে তোমাদের ভালো লাগার কথা নয়। সময় বদলে গেছে, মানুষ বদলে গেছে, মানুষের জীবনদর্শন বদলে গেছে। তবু, কী জানি? পড়ে দেখো। কেমন লাগল, তা জানালে খুব খুশি হব। প্রশংসার কাঙাল নই আমি। তোমার এখন যেমন বয়েস, তখন আমার বয়েসও সেরকম ছিল। অন্য প্রজন্মের একজন মানুষের চোখ…
চিঠি কেন, এখানেই পড়ে নিজেই এসে আপনকে জানিয়ে যাব কেমন লাগল।
বৃদ্ধ বললেন, না, না। মুখে জানিয়ো না। চিঠিই লিখো।
আমি অবাক হয়ে বললাম, কেন?
ভালো বা মন্দ, কোনো বিশেষ কথা কাউকে মুখে বলা যায় না। বলা উচিতও নয়। কারণ, কথার পিঠে কথা ওঠে। কারণ, যাকে তা বলা হচ্ছে তার মুখের অভিব্যক্তি এবং কথায় ও প্রতিক্রিয়ায় সব কথা সঠিক ভাবে বলে ওঠা হয় না। চিঠিই ভালো। তোমাকে কেউ বাধা দেবে না, তোমাকে মূর্খ বললে, পাগল বললে, তুমি ইন্টারাপটেড হবে না। চিঠিই হচ্ছে শিক্ষিত মানুষের সবচেয়ে বড়ো শিক্ষা। হয়তো ছবি আঁকা বা গান গাওয়ার চেয়েও বড়োতা। চিঠিতে আমরা একে অন্যকে যেভাবে ছুঁতে পারি অন্য কিছুতেই তেমন পারি না। এমন কী…
আমি বললাম, কী?
এমনকী হয়তো সংগমেও না।
আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। বৃদ্ধর আধুনিকতায়।
উনি বললেন, চিঠির কোনোই বিকল্প নেই। এটি পড়ে যা তোমার মনে হয় নির্দ্বিধায় তা আমাকে চিঠিতেই জানিয়ো। আমার কাছে যা ফসিল হয়ে গেছে তা থেকে তুমি হয়তো দু এক গাছি মৃতপ্রায় লাল হয়ে-যাওয়া ঘাস খুঁটে নিলেও নিতে পারো। আসল কথাটা হচ্ছে; কমিউনিকেশান। চল্লিশ বছর তো মস্তই ব্যবধান!
আমাকে পড়তে দিন। আগে কিছুই বলবেন না। আমি বায়াসড হয়ে যাব।
ঠিক বলেছ।
বলেই বললেন, একটু দাঁড়াও ভাই। নিয়ে আসি ভেতর থেকে।
বৃদ্ধ ভেতরে চলে গেলেন মাথা ঝুঁকিয়ে মাটির-দাওয়া পেরিয়ে শনে-ছাওয়া ঘরের অন্ধকার অভ্যন্তরে।
উঠোনের পাশে একটি বড়ো কুচিলা বা নাক্সভোমিকা গাছ ছিল। তার মগডালে বসে একজোড়া বড়কি-ধনেশ হ্যাঁ হ্যাঁক হঁক হঁক করে কথা বলছিল। এই পাখিগুলো বড় শব্দ করে। যেখানেই থাকে। আফ্রিকার জলহস্তীরা যেমন। এই পাখি আর এই জানোয়ারের সঙ্গে পৃথিবীর সব মানুষদের বড়োই মিল।
বৃদ্ধ ঘর থেকে আবার কুঁজো হয়ে বেরিয়ে এলেন। একটি বাঁশের চাঁচ দিয়ে তৈরি চারকোনা খাঁচা নিয়ে। সেটা নিয়ে এসে, আমি যে কাঠের টুলে বসেছিলাম, তার ওপর রেখে বললেন, একটু দাঁড়াও ভাই, দড়ি দিয়ে বেঁধে দিই। এটাকে নেবে কী করে?
বললাম, কিচ্ছু করতে হবে না। আমি বগলদাবা করেই নিয়ে যাব।
তা না হয় যেয়ো, একটু দাঁড়াও। ধুলোটা ঝেড়ে দিই অন্তত।
ওঁকে নমস্কার করে বললাম, যাই।
বৃদ্ধ বললেন, যাই বলতে নেই! এসো।
.
০৪.
দুপুরবেলা অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে উঠলাম। বিকেলে চা খেয়ে বাংলো থেকে কিছুটা গিয়েই নদীরেখা ধরে হাঁটতে গেলাম। শীতের দুপুরে ঘুমিয়ে গা-হাত-পা ম্যাজম্যাজ করছিল।
শীতের পাহাড়ি নদীর রূপই আলাদা। সাদা বালি, কালো পাথর, দু-পাশের ঝুঁকে-পড়া ঘন সবুজ গাছ-গাছালির মধ্যে স্বচ্ছ জলধারা মৃদু গুঞ্জনে বয়ে চলেছে, এঁকে-বেঁকে গেছে নদী। প্রতি বাঁকেই বৈচিত্র্য।
কিছুটা এগিয়ে যাওয়ার পরই বালিতে চান্দা রাজার পায়ের দাগ দেখলাম। একটু এগোতেই দেখলাম, যে-পাহাড়ে আমরা সেদিন ছুলোয়া করেছিলাম সেই পাহাড় থেকেই নেমে আসা একটি জানোয়ার-চলা পাকদন্ডী পথ নদীটিকে পেরিয়ে বিপরীত দিকের প্রান্তরে চলে গেছে। এদিকে হয়তো কখনো ক্লিয়ার-ফেলিং হয়ে থাকবে। চমৎকার ঘাসি প্রান্তরের সৃষ্টি হয়েছে। কানহা-কিমলির জঙ্গলে যেমন আছে। যে জায়গাতে জানোয়ার-চলা পথটি নদী পেরিয়েছে ঠিক সেইখানেই নদীর পাশে, প্রান্তরের দিকে একটি মস্ত অশ্বথ গাছ। এই গাছে। বিকেলে অথবা চাঁদনি রাতে একটু ধৈর্য ধরে বসলেই, নদী পেরিয়ে চান্দা-রাজা যখন প্রান্তরে ঢুকবে অথবা প্রান্তর থেকে ফিরবে তখন তাকে সহজেই কবজা করা যেত। তার বাঁচার কোনো পথই থাকত না। আমার চলে-যাওয়া বন্ধুদের কথা মনে পড়ে মনটা খারাপ হয়ে গেল। চান্দা-রাজার জন্যে ওরা কম কষ্ট করেনি।
কিন্তু বৃদ্ধ বাঙালিবাবুর সঙ্গে আজ সকালে দেখা ও কথা হওয়ার পর থেকেই শিকার থেকে আমার নিজের মনটা সরে আসতে চাইছে। অবশ্য রাতারাতিতেই সুবোধ হতে পারব না যে তা জানি। তবুও বৃদ্ধর কথা যে আমাকে দারুণভাবে বিচলিত করেছে, মানে তাঁর শিকার বিরোধিতার কথা; তাও অস্বীকার করতে পারি না।
ওই অশ্বত্থ গাছে উঠে বসলে হয়তো আজই সন্ধের আগে চান্দা-রাজাকে দেখা যেত। যদি শিকার নাও করি, চান্দা-রাজার মতো একটি বাঘকে চোখে দেখাও কম কথা নয়। ভাবলাম, এখানে তো আছি আরও ক-দিন। বসব না হয় রাইফেল ছাড়াই এসে। কিন্তু আজ নয়। আমার মন পড়ে আছে বাঙালিবাবুর ডায়েরির দিকে। কী আশ্চর্য টান যে অনুভব করছি তা বলার নয়। মনে লাগার আগেই বাংলোতে ফিরে হ্যাঁজাকটি সামনে রেখে সেই ডায়েরি পড়া আরম্ভ করব।
বাংলোতে ফিরতেই চৌকিদার এবং গুরবা বলল, রাতে কী রান্না হবে?
বললাম, খিচুড়ি বানাতে। মুগের ডালের ভুনি-খিচুড়ি। সঙ্গে আলু ও ডিম-ভাজা। আরও বললাম ওদের যে, খাওয়া লাগাবার অন্তত পনেরো মিনিট আগে আমাকে বলে দেবে।
ওদের একথা বলেই, ধড়াচূড়া ছেড়ে পায়জামা, গরম-পাঞ্জাবি, গরম-জওহরকোট আর শাল গায়ে দিয়ে এসে বসলাম টেবিলে। তারপর খুলোম সেই ডায়েরির প্রথম পাতা।
.
কী জানি! কোন ভাগ্যলিপি আমাকে এই শালডুংরিতে টেনে নিয়ে এল। এত বছর ধরে যা কিছুকেই দামি বলে মনে করেছিলাম তার সবকিছুকেই ছেড়ে আসতে হল কার অদৃশ্য অঙ্গুলিহেলনে!
ওরা সকলেই চলে গেছে। আমি রয়ে গেলাম। পেছন থেকে কে বা কেউ যেন আমায় তীব্রভাবে আকর্ষণ করে আমাকে এখানে রেখে দিল। সে কে বা কারা, কে জানে?
এতদিন, দেশে ও বিদেশে তো শুধু এগিয়ে চলার তাগিদ নিয়েই বেঁচেছিলাম। পশ্চিমের শিক্ষার মূলকথাও তো তাই-ই। কিন্তু কী যে হয়ে গেল…
-সেদিন নদীর বালিতে পূর্ণিমারাতে হনসোকে আদর করলাম। নারী-শরীরের স্বাদ তো এই প্রথম নয়। দেশে থাকতে অবশ্য কোনো অভিজ্ঞতাই হয়নি। বিদেশেই প্রথম হয়েছিল। তারপর একাধিক বার। কিন্তু রাত-পাখির ডাকের মধ্যে, আমার দেশের মাটিতে, আমার দেশের মেয়েকে আদর করার মধ্যে দিয়ে মনে হল যেন আমি শুধু আমার দেশকেই নয়, সমস্ত বিশ্বকেই আবিষ্কার এবং উপলব্ধি করছি। মিলন যাদের কাছে নিছকই শারীরিক আনন্দ, মনের গভীর অভিব্যক্তি নয়; তারা বোধ হয় মানুষ-পদবাচ্য এখনও হয়ে ওঠেনি।
আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনম সামান্যমেতাৎ পশুভি: নরানাং।
ধর্মহি তেষাম অধিকো বিশেষো : ধর্মেণ হীনা পশুভিসমানাঃ।
হিতোপদেশের কথা।
মানুষের সঙ্গে পশুকে মানুষের ধর্মই পৃথক করে রেখেছে। নইলে মানুষ আর পশু অনেক ব্যাপারেই সমান।
হনসো ফিস ফিস করে কথা বলছিল।
কথা নয় ঠিক, স্বগতোক্তি।
সব মানুষই চরম দুঃখে অথবা আনন্দে যেমন করে কথা বলে…
মন্থর হাওয়াতে কত নাম-না-জানা ফুলের গন্ধ ভাসছিল। বন-জ্যোৎস্নায় বিভিন্ন গাছেও বিচিত্র ছায়ারা কেমন এক মোহাবরণ সৃষ্টি করেছিল। আমি নদীর বালিরেখা ধরে বহুদূর অবধি, যেখানে নদীটা বাঁক নিয়েছে সেই বাঁকের দিকে চেয়েছিলাম। একটি পাথরে হেলান দিয়ে আধোশুয়ে।
অত দূরে চোখে স্পষ্ট কিছুই দেখে না। বন-জ্যোৎস্না, বনছায়া, হাওয়াতে ঈষৎ আন্দোলিত করোঞ্জ-এর ঝাড় সব মিলিয়ে ওই নদীর বাঁকটিকে ভারি রহস্যময় করে তুলেছিল।
হনসো আমার কোলে মাথা রেখে টান-টান হয়ে শুয়েছিল আদর খাওয়ার পর। এই বনেরই মতো, বনের মেয়েদেরও যেন রহস্যের শেষ নেই। যদিও নিরাবরণ, তবুও দুধলি আলো আর কাঁপা-কাঁপা ছায়ার আল্পনা খুবই কাছে থাকা তার শরীরটিকেও বড়ো দূরের করে তুলেছিল। ওর শরীরের স্পর্শ পাওয়া সত্ত্বেও মনে হচ্ছিল ও যেন নদীর ওই দূর বাঁকেরই মতো রহস্যময়। কোনোদিনও বোধ হয় পুরোপুরি ওর মন অথবা শরীর দুইয়ের কোনোটিকেই জানা হবে না। ছোঁওয়া যাবে না।
আসলে যা কিছুই প্রকৃত সৌন্দর্যের ধারক এবং বাহক তা বোধ হয় এইরকমই হয়। রহস্যময়তাই বোধ হয় সৌন্দর্যের মূলরহস্য।
এডগার অ্যালান পো রিয়ালিজমকে সহ্যই করতে পারতেন না। পোর কাছে আর্ট ছিল– ওনলি বিউটি। অ্যাণ্ড টু বিউটি ওলওয়েজ কনটেইনড অ্যান এলিমেন্ট অফ স্ট্রেঞ্জনেস অর ভেগনেস।
কোথায় যেন পড়েছিলাম, ইংল্যাণ্ডে থাকতেই, যে চার্লস বোদলেয়ারের মতো বড়ো স্বতন্ত্র ফরাসি কবিও বলেছিলেন : এডগার অ্যালান পো ওজ আ সেইন্ট।
যে রহস্যময়তার কথা আমি বলছি, যে সৌন্দর্যময় রহস্যময়তা সেদিন রাতে একটি যুবতী শরীরের চারিয়ে দেওয়া সুখের সঙ্গে আমার শরীর এবং মনের মধ্যেও অশেষ আশ্লেষে চারিয়ে গেছিল, তা বুঝি মুনি ঋষিদেরই অনুভবের। আমার মতো সাধারণ একজন মানুষের বহুজীবনই কেটে যাবে এই ভয়ংকর সুন্দর রহস্যময়তার গভীরে গিয়ে তার প্রকৃত সত্তাকে জানতে জানতে।
সকালে বেড়িয়ে এইমাত্র ফিরলাম।
হনসো আমার ঘুম ভাঙার অনেকই আগে উঠে পড়ে। তারপর আমাকে ওঠায়। চা খাওয়ার মতো সামান্য শখটিও কী নিঃশব্দে মরে গেল। আমার চারপাশেই এখন অনেকই রকম অভ্যেসের কঙ্কালগুলি স্তূপীকৃত হয়ে আছে। কঙ্কাল না দেখলে হয়তো অভ্যেসগুলির অপ্রয়োজনীয়তা এমন করে প্রতীয়মানও হত না।
তবে চা পাওয়া গেলে খাওয়া চলতও হয়তো। নেশা বা কোনো কিছুর অভ্যেস খারাপ নিশ্চয়ই। কিন্তু এইসব সম্বন্ধে বাড়াবাড়িরকমের কাঠিন্যও আমার পছন্দ নয়। আমি যেকোনো নেশাকেই পেতে পারি। পেয়েও ছিলাম অনেক নেশাকে। কিন্তু কোনো নেশা আমাকে পেয়ে বসবে এটা হওয়ার নয়। যখন নেশা করতামও অনেকই রকমের, তখনও জানতাম যে যেমন করে ধরেছি তেমন করেই হঠাৎ-ই ছেড়ে দেব। তবে এত তাড়াতাড়ি যে তা করব তা আগে জানা ছিল না।
জীবনটা একেবারেই বদলে গেল। যে জীবনের প্রার্থনা ছিল তা পেয়েও ছিলাম। গায়ে ভালো-দোকানে-বানানো অর্ডারি জামার ই মতো তা বেমানানও হয়নি। কাঁধ থেকে গোড়ালি, জামার কলার থেকে ট্রাউজারের ফোল্ড অবধি মাপ সব ঠিকঠাকই ছিল। কিন্তু রাতারাতি আমি মানুষটাই সংকুচিত হয়ে যাওয়ায় জামাগুলি সব ঢিলে হয়ে গেল। ফেলে দিতে হল তাদের।
শুধু আমারই নয়, এই বনে-পাহাড়ে আজ তিনমাস থাকার পর, হনসোদেরই একজন হয়ে যাওয়ার পর আমি বুঝতে পারি যে, আমাদের মতো শহুরে শিক্ষিত মানুষেরা যে জীবনের কামনা করি শিশুকাল থেকে, যারজন্যে প্রাণপাত করি, দেশে-বিদেশে জ্ঞানার্জনের জন্যে দৌড়োই সেই ফাঁপানো-ফোলানো জীবনের কিছুমাত্রই দরকার ছিল না একজন মেদহীন, ঋজু, এবং সৎ-মানসিকতার সরল স্বভাব ও সহজ অভ্যাসের মানুষের।
কিন্তু আমি যা বুঝছি, তা অন্যকে বোঝাই কী করে?
দরকারই বা কী? নিজে যে যা বুঝল, তাই-ই বুঝল।
একজন মানুষ অন্য মানুষকে এইসব গভীর ব্যাপারে কিছু বোঝাতে পারে না। ভোট চাইবার জন্যে, যশ চাইবার জন্যে, বক্তৃতাবাজি বা ভিক্ষে চাইবার জন্যে ভন্ডামি-সর্বস্ব কাকুতি তো এ নয়! নিজের ভেতর থেকে বোঝার তাগিদ না এলে, সময় উপস্থিত না হলে, এইসব বোঝা-বুঝি নিয়ে ধ্বস্তাধ্বস্তি করে লাভও হয় না কিছু। কেউ বা জীবনের শেষে পৌঁছে জীবনটা তার প্রার্থিত জীবনের মাপমতো হল কি হল না তার খোঁজ করার প্রয়োজন অনুভব করে। অনেকে বা অনেক জীবন পেরিয়ে এসেও তার প্রয়োজন বোধ করে না। প্রত্যেক মানুষের রকম ও প্রকৃতিই যে আলাদা! যে যেমন, তাকে তেমন থাকতে দেওয়াই বোধ হয় ভালো।
এসব জিনিসে তাড়াহুড়ো করতে নেই। করা উচিতও নয়।
নিজের নিজস্বতাকে, জীবনের সাহসিতাকে, ঈশ্বর-বোধকে একজীবনে যদি জানা না যায়, উপলব্ধি করা না যায়, তবে নাই-ই বা গেল। যা সময় লাগে, দিতে হবেই। ভাত ফোঁটার সময়েরই মতো।
সব ব্যাপারে তাড়াহুড়ো বা শর্টকাট চলে না।
আজ গেছিলাম বিরহী গ্রামে। ওখানে বনবিভাগের তত্ত্বাবধানে বিন্দিয়া নদীর পাশে একটি তালাও খোঁড়া হচ্ছে। শালডুংরির অনেকেই গেছে দিন-মজুরি করবে বলে।
হনসোও যেতে চেয়েছিল, কিন্তু ছ-মাস হল গর্ভবতী হয়েছে। আমিই যেতে দিইনি। যে ক-বছর আমার পুঁজি ট্যাঁকে, সে ক-বছর ওকে একটু আরাম দিই। তারপরে দেখা যাবে।
দুপুরের অবসরে ওরা সবাই নদীর পারে বসে খাচ্ছিল। সকলেই বাড়ি থেকে ভাত নিয়ে এসেছে। কেউ একটু তরকারি, কেউ বা শুধুই নুন। শালপাতা ছিঁড়ে দোনা বানিয়ে তাতেই ঢেলে খেল ভাত। তারপর নদীতে জল খেল। খাওয়া-দাওয়ার পর গাছতলায় সকলেই মিনিট পনেরো গড়িয়ে নিল মেয়ে-পুরুষ। চুট্টা খেল কেউ কেউ। তারপর আবার কোদাল গেঁইতি হাতে নিয়ে লেগে পড়ল।
ওদের দেখে ভাবছিলাম যে, ওদেরই মতো পৃথিবীর সব মানুষের জীবনযাত্রাই খুব সরল সহজ হওয়ার কথা ছিল। হয়তো এরকম সুখের হওয়ারও কথা ছিল। মানুষ নিজেই দিনে দিনে তাকে বড়ো গোলমেলে করে তুলে, নিষ্প্রয়োজনের প্রয়োজনের আধিক্যে মুড়ে ফেলে এখন তার নীচে চাপা পড়ে মরছে।
প্রকৃতি পশুপাখিরই মতো, মানুষকেও তার জীবনধারণের সমস্ত মূলউপাদান দিয়ে রেখেছিলেন। অন্য সব প্রাণীরই কুলিয়ে গেল, শুধুমাত্র মানুষেরই কুলেল না তাতে। নিত্যনতুন চাহিদায় ভাবনাহীন, গতি-সর্বস্ব এক জীবনকে সে আঁকড়ে ধরল। আধুনিক, বিজ্ঞানবিশ্বাসী, হাজার আরামে অভ্যস্ত শহরবাসী আধুনিক মানুষের মুক্তির কোনো উপায়ই বোধ হয় আর নেই। সে থামবে শুধুমাত্র নিজের ধ্বংস সম্পূর্ণ হলেই; সর্বনাশ নিশ্চিন্ত হলে। এই আত্মহত্যাকামী, পন্ডিতমন্য মূর্খদের অন্যে যে বাঁচাবে এমন হওয়ার জো-ও নেই। নিজের মৃত্যুকে সে নিজেই আবাহন করে এনেছে। আলিঙ্গন করছে মৃত্যুকেই জীবন মনে করে।
আমি জানি, এসব কথা বলতে গেলে কলকাতায় আমার শিক্ষিত বন্ধুবান্ধবেরা আমাকে উন্মাদ বলবে। বলবে, হনসো নাম্নী মুণ্ডা মেয়েটি আমার মাথাটি চিবিয়ে খেয়েছে। কেউ বা বলবে, দানোতে পেয়েছে আমাকে। কী করে আমি বোঝাব ওদের যে, আমি যে আজ বিশ্বাস করে হাসিমুখে এই জঙ্গলের জীবনকে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করলাম ওরা অথবা ওদের বংশধরেরা সকলেই আজ থেকে পঞ্চাশ বা পঁচাত্তর বছর পরে এই জীবনকেই গ্রহণ করবে বাধ্য হয়ে কাঁদতে কাঁদতে।
সময়ই বলবে, আমিই ঠিক না ওরা।
কাল মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেল। দরজা খুলে দাওয়াতে এসে বসলাম। কাক-জ্যোৎস্নায় ছমছম করছে বন-পাহাড়। কোকিল ডাকছে মুহুর্মুহু। পিউ-কাঁহা পাখিও। ঝিরঝিরে বাতাসে শুকনো পাতারা ইতস্তত উড়ে বেড়াবে একটু পরে।
মাঝরাতে হাওয়া থাকে না। কেমন একটা থম-মারা ভাব। এখনও রাতে শিশির পড়ে এখানে। ঝরা পাতারাও এখন ভারী। রোদ ওঠার পরে এবং বিশেষ করে দুপুরের দিকে এরা আবার ভারশূন্য হয়ে বনের বুকে মচমচানি আওয়াজ তুলে পাথরে পাথরে ছুটে বেড়াবে। হাওয়াতে নয়, এই স্তব্ধ আবহাওয়াতে মহুয়া আর করৌঞ্জের গন্ধও থম মেরে আছে। গন্ধ উড়লে একরকম আর স্থির থাকলে অন্যরকম। বনের গভীরে যাঁরা না থেকেছেন তাঁরা তা জানবেন না।
আকাশ ভরা তারা ঝকঝক করছে চৈত্রের মধ্য-রাত্রির আকাশে। মাথার ওপর দিয়ে একঝাঁক রাতপাখি, হেরন, তাদের গম্ভীর গলার ওয়াক ওয়াক ডাক ডাকতে ডাকতে উড়ে চলে যাচ্ছে। তাদের ঘাড়ের কেশর চকচক করছে চাঁদের আলোয়।
রবীন্দ্রনাথের সেই একটা গান ছিল না। ওদের কথায় ধাঁধা লাগে তোমার কথা আমি বুঝি, তোমার আকাশ তোমার বাতাস এই তো সবই সোজাসুজি। এমন এমন মুহূর্তে ওই গানটির কথা মনে হয় আমার। তাঁকে বুঝতে হলে, অন্তরে উপলব্ধি করতে হলে মন্দিরে মসজিদে গির্জেতে ঘোরাঘুরির দরকার কী? যে বোঝে সে তাঁকে এমনি সহজ করেই বোঝে। দাপিয়ে বেড়াতে হয় না পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত। সমাহিত, শান্ত না করতে পারলে নিজেকে, তাঁকে বোঝার কোনো উপায়ই নেই। ঘোলা-জলে তো প্রতিবিম্ব পড়ে না। জল থিতোলে তবেই তা স্বচ্ছ হয়। স্বচ্ছ মন, স্বচ্ছ কলুষহীন মানসিকতা ছাড়া ঈশ্বরবোধ তো সম্ভবে না।
আমার লাইব্রেরির সব বই পরশু এসে পৌঁছেছে এখানে। সুরেশ ওয়াগানে লোড করে দিয়েছিল বি এন আর-এর ট্রেনে। রায়পুর স্টেশন থেকে ট্রাক ভাড়া করে অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে এনেছি এখানে। মাটির ঘরে কাঠের তাকে দু-দিন ধরে সব বইগুলি গুছিয়েছি। এখানে বড়ো উই আছে। ওরা বলে দীমক। বইগুলো সব কেটে না দেয় উইয়ে।
বই ছাড়া, চোখ ছাড়া বেঁচে থাকার কথা ভাবতে পর্যন্ত পারি না।
সেদিন পড়ছিলাম, রবীন্দ্রনাথের চিঠি, তাঁর পুত্রবধূকে লেখা, শ্রীঅরবিন্দর সঙ্গে পন্ডিচেরিতে দেখা হওয়ার পর। উনিশ-শো আটাশ সনের মে মাসে লেখা। ভারি ভালো লাগল পড়ে।
রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :
স্থির করেছি এবার ফিরে গিয়ে অরবিন্দ ঘোষের মতো সম্পূর্ণ প্রচ্ছন্নতা অবলম্বন করব। কেবল প্রতি বুধবারে সাধারণকে দর্শন দেব। বাকি ছ-দিন চুপচাপ নিজের নিঃশব্দ নির্জন শান্তি অবলম্বন করে গভীরের মধ্যে তলিয়ে থাকব–অরবিন্দকে দেখে আমার ভারি ভালো লাগল। বেশ বুঝতে পারলুম নিজেকে ঠিকমতো পাবার এই ঠিক উপায়…।
ঠিক করেছি এখন থেকে দীর্ঘকাল প্রচ্ছন্ন থাকব। কারো সঙ্গে কোনো কারণেই দেখা করব না, কেবল বুধবার দিনে নিজেকে প্রকাশ করা যাবে। আত্মীয়দের চিঠি ছাড়া চিঠি পড়ব না। গভীরভাবে সম্পূর্ণভাবে নিজেকে নিয়ে থাকব। যদি লেখা জমে আসে তো লিখব। পন্ডিচেরিতে অববিন্দর সঙ্গে দেখা করে আমার মনে হল আমারো কিছুদিন এই রকম তপস্যার খুব দরকার। নইলে ভিতরকার আলো ক্রমশঃই কমে আসবে। প্রতিদিন যা-তা কাজ করে যা-তা কথা বলে মনটা বাজে আবর্জনায় ঢাকা পড়ে যায়। নিজেকে দেখতেই পাইনে….
এইরকমই একটা কথা পড়েছিলাম আঁদ্রে মরোয়ার (মালরো নয়) একটি বইয়ে। বইটির নাম ছিল দ্য আর্ট অফ লিভিং। তাতে মরোয়া বলেছিলেন যে, যারা কাজের লোক, যাদের জীবনে কোনো বিশেষ ব্রত আছে তাদের এ বাবদে নিষ্ঠুর হতেই হবে। চিঠি লিখে, ফোন করে, বাড়িতে এসে যেসব লোক বিরক্ত করে, কাজের বিঘ্ন ঘটায়, তাদের প্রতি কঠোর মনোভাব নিতে হবে, নইলে কাজটাই হবে মাটি। এই ছোট্ট জীবনে নষ্ট করার মতো সময় কোথায় মানুষের?
মরোয়া ওই সময়-নষ্টকারী মানুষদের নাম দিয়েছিলেন ক্রনোফেজেস।
যাঁরা জননেতা, বা অভিনেতা বা জনগণের অন্য কোনো ব্যাপারের প্রতিভূ তাঁদের কথা আলাদা। কারণ তাঁরা বহির্মুখী। তাঁদের দৌড়ে যাওয়া বাইরের দিকে। আর যাঁরা আমার মতো জঙ্গলে এসে স্বেচ্ছাতে বাস করেন তাঁদের যা কিছু দৌড় তো ভেতরে ভেতরেই। অন্তর্মুখীনতাই তাঁদের জীবনের সব সুখের চাবিকাঠি। কে যে জীবনে কী চায় এই সরল সত্যকে হৃদয়ংগম করতে করতেই জীবন পেরিয়ে যায়, চাওয়াটা তাই প্রায়শই পাওয়াতে পর্যবসিত হয়ে উঠতে পারে না।
উনিশশো উনত্রিশে, রবীন্দ্রনাথ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লিখেছিলেন, (প্রবাসী সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়) কলম্বো থেকে :
দেশে গিয়ে সম্পূর্ণ নির্জনবাসের মধ্যে তলিয়ে গিয়ে দীর্ঘকাল বাক্য ও কর্ম থেকে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি নেব ঠিক করেছি। ছোটো ছোটো দাবির শিলাবৃষ্টিতে আমার দেহমনের সমস্ত ডাঁটাগুলোএকেবারে আলগা হয়ে গেছে। ডাক্তার বলছে স্থির হয়ে থাকা ছাড়া আর ওষুধ নেই। অন্তরের মধ্যে তার একান্ত প্রয়োজনও বোধ করচি…
নিজের কর্মক্ষেত্র থেকে বাইরে এলেই, একটু নির্জনতা পেলেই বোধ হয় কর্মী মানুষদের মনে নতুন নতুন ভাবের আগমন ঘটে। নতুন নতুন স্বপ্ন, পরিকল্পনা, প্রত্যয় শিকড় পায়। তবে দেখা যায় ফিরে যাওয়ার পর আবারও তাঁর নিজের জীবনের দৈনন্দিনতার ঘেরাটোপে তিনি আটকে পড়ে যান। বড়ো মানুষদেরও দৈনন্দিনতার দৈন্য থাকেই, অরবিন্দও বড়ো রবীন্দ্রনাথও বড়ো তবে অরবিন্দ অন্তরের গভীরে যতখানি বড়ো রবীন্দ্রনাথ সেই গভীরে পৌঁছোতে পারেনি কারণ তিনি লেখক ছিলেন, কবি এবং গায়কও। গান কবিতা এবং লেখা শ্রোতা এবং পাঠকদের বাদ দিয়ে চলে না। অরবিন্দর সাধনা ছিল পুরোপুরিই অন্য-নিরপেক্ষ সাধনা। অন্য কাউকেই তাঁর প্রয়োজন ছিল না কোনোই। তাই তিনি ছোটো ছোটো দাবির শিলাবৃষ্টিতে দেহমনের ডাঁটাগুলো আলগা হওয়া হয়তো রোধ করতে পেরেছিলেন।
কেন জানি না, আমার এই বয়েসেই এমন মনোভাব হল। লোকে আমাক জ্যাঠা বলতে পারেন। কিন্তু জ্যাঠা যদি একদিন হতেই হয় তবে আগে হতেই বা ক্ষতি কী?
বড়ো বড়ো মনীষীরা সকলেই কিন্তু এই নির্জনে পালিয়ে যাওয়ার তাগিদ বোধ করেছেন। টলস্টয় বার বার চেষ্টা করে শেষে সমস্ত সম্পত্তি স্ত্রী এবং ছেলেদের লিখে দিয়ে চলে গেছিলেন মাটির কাছে। স্ত্রী এবং ছেলেরা তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন। কে আর বৈভব ছেড়ে স্বেচ্ছায় গরিব হতে চায়? অথবা যাঁকে জড়িয়ে তাঁদের বৈভব তাঁকে গরিব হতে দিতে চায়? এক সকালে স্ত্রীকে একটি ছোট্ট চিঠি লিখে চলে গেছিলেন টলস্টয়। সাধারণ চাষির জীবন বেছে নিয়েছিলেন। নিজে হাতে খেতের কাজ করতেন।
আমি কোনোদিক দিয়েই বড়ো নই। বড়ো হওয়ার কোনো সম্ভাবনাও আমার নেই। শুধু অনেক বড়ো মানুষের মানসিকতার সঙ্গে একাত্মবোধ করি। এই পর্যন্ত। শুধু মানসিক একাত্মতা থাকলেই বড়োর সমকক্ষ হওয়া যায় না।
এই নিস্তব্ধ সুগন্ধি রাতে একা বসে কত কী ভাবতে ইচ্ছে যায়। ঘরের মধ্যে আমার গর্ভিণী আদিবাসী স্ত্রী পাশ ফিরে শুয়ে আছে। তার গায়ে এই সুগন্ধি ধরিত্রীর গন্ধ। তার বাহুমূলের, ঊরুসন্ধির গন্ধে আমি আমার দেশের যুগযুগান্তরের মাটির গন্ধ পাচ্ছি, সোঁদা সোঁদা। মাটি যেমন করে মাটিতে জন্মায়, জীবন যেমন করে মৃত্যুতে মাটি হয়ে জায়মান হয়, তেমনি মৃত্তিকাগন্ধি জীবনই আমি কামনা করি। ন্যুট হামসন-এর গ্রোথ অফ দ্য সয়েল বইয়ে যে বিদ্যুৎ আর কুয়াশার কথা আছে আমি তেমনই কুয়াশা হয়ে যেতে চাই। বিদ্যুৎ-এর মধ্যে এস্ততা আচে। হঠাৎ চমক আছে, প্রচন্ড শক্তি তারমধ্যে চকিতে জ্বলে উঠেই নিভে যায়। কিন্তু বিদ্যুৎ নিজের ইচ্ছেতে চমকে উঠতে পারে না। সে পর-ইচ্ছাধীন। আমি কুয়াশা হতে চাই। সবকিছুকে মুড়ে পক্ষপুটে ঢেকে নিয়ে, স্পষ্টতার দৈন্য অস্পষ্টতার ঐশ্বর্যে মাখামাখি করে কোনো জাপানি শিল্পীর ওয়াশের কাজের ছবিরই আবেশের মতো, জীবনকে একটি মুর্শিদাবাদি আতরগন্ধি বালাপোশেরই মতো আশ্লেষে গায়ে জড়িয়ে কাটাতে চাই আমার বাকি জীবন। এই জীবনের উষ্ণতা, শৈত্য, হতাশা এবং সারল্য সবকিছুই আমার পরবর্তী প্রজন্মকে, আমার উত্তরসূরিদের যেন ছুঁয়ে যায়। আমি যা ছেড়ে এসে যা পেয়েছি ওরা যেন সেই ছেড়ে আসাকে মূর্খামি বলে না ভেবে আমাকে আমার স্বকীয়তা এবং সাহসের জন্যে একদিন সাধুবাদ দেয়। সব চেয়ে বড়ো কথা, ওরা যেন এই জীবনে সম্পৃক্ত হতে পারে। এই জীবনের নীরব আশীর্বাদ, এই রাতের স্নিগ্ধ শান্তি যেন ওদের ধন্য এবং স্নিগ্ধ করে। ওরা যে সময়ের পৃথিবীতে বাস করবে সে পৃথিবীর জ্বালা আরও অনেক বেশিই হবে আজকের পৃথিবীর থেকে। ওরা যেন প্রকৃত সুখ কী এবং কোথায় তা বুঝতে ভুল না করে।
.
০৫.
মার্গারেটের কথা আজ সকাল থেকেই খুব মনে পড়ছে।
আজ ওর জন্মদিন। ওখানে থাকলে মিডেক্স-এ ওদের বাড়ির পার্টিতে যেতাম রাতে। দুপুরে ওকে নিয়ে কোথাও লাঞ্চ খেতাম।
মার্গারেট খুবই দুঃখ পেয়েছিল। অথচ দুঃখ কিন্তু আমি দিতে চাইনি। ওর পক্ষে সম্ভব ছিল না আমার সঙ্গে কলকাতায় আসা। এবং থাকা। ওর মনে আমার প্রতি ভালোবাসাটা এমন তীব্র ছিল না যে, ও ওর নিজের নিজস্বতা এবং ওর স্বজাতির সমস্ত স্বকীয়তা বিসর্জন দিয়ে পুরোপুরিই ভারতীয় হয়ে বাকি জীবন কলকাতাতেই কাটাতে পারত।
আমার বেলাতেও সেকথা প্রযোজ্য ছিল। যেসব ভারতীয় মেমসাহেবের ভালোবাসা পেয়েই নিজেদের কৃতার্থ বলে মনে করেন এবং নিজের কৃষ্টি, ভাষা, সাহিত্য, নিজের সমস্ত নিজস্বতাই বিসর্জন দিতে রাজি থাকেন তাঁকে নিয়ে ঘর করার জন্যে আমি তাঁদের দলে নই। একজন নারীর জন্যে আমার স্বদেশ ও স্বকীয়তা আমি ছাড়তে রাজি ছিলাম না। মার্গারেটও তেমন মানসিকতার ছিল না। এবং ছিল না বলেই ওকে আমি সম্মান করতাম। ও-ও হয়তো সম্মান করতো আমাকে ওরই মতো করে।
যা বললাম, তা অবশ্য সাধারণদের কথা। অসাধারণ মানুষেরা এই সাধারণ নিয়মে পড়ে না। তাঁরা একে অন্যের প্রতিবন্ধক হন না বরং পরিপূরক হন। আমি ও মার্গারেট সাধারণ মানুষ বলেই পারিনি তেমন ঝুঁকি নিতে।
এখানে হনসোকে বিয়ে করে এই গহন জঙ্গলের মধ্যে ঘর বাঁধার পরে মার্গারেটকে চিঠি লিখেছিলাম আমার সুখানুভূতি এবং এই নতুন জীবনের কথা জানিয়ে। ওকে যে মনে পড়ে সেকথাও জানিয়ে।ওকে লিখেছিলাম যে,
যে কারণে তোমরা সঙ্গে ঘর বাঁধা হল না সেই কারণটাকেই অতিক্রম করে যেতে পেরে ভারি আত্মস্থ, সমাহিত বোধ করছি। এখন আমি ভালো করলাম কী খারাপ তা জানি না।
শুধু মাত্র ভালো থাকা, ভালো খাওয়া, ভালো পরা অন্য সব মানুষই যা করে তা করার একঘেয়েমি ও কামনা থেকে নিজেকে এই অসময়ের বানপ্রস্থে নির্লিপ্তির সঙ্গে নিয়োজিত করে ভারি একটা আনন্দ বোধ করছি, যেমনটা লণ্ডনে বা কলকাতায় থাকলেও বোধ হয় কখনো বোধ করতাম না।
তোমার সঙ্গে আমার সংস্কৃতিগত, ভাষাগত, জীবনযাত্রাগত যতটুকু অমিল ছিল, হনসোর সঙ্গে হয়তো তার চেয়েও অনেক বেশি অমিল। কিন্তু আসল ব্যাপারটা হচ্ছে প্রকৃতির সান্নিধ্য। আমাদের দেশের অরণ্যপর্বতের সৌন্দর্য, ভারতীয় প্রকৃতির গহন গভীর রহস্যময় স্বরাট ব্যক্তিত্বর স্বরূপ তোমাদের দেশে বসে তোমরা ভাবতে পর্যন্ত পারো না। আমাদের মুনি, ঋষি, দার্শনিকেরা হাজার হাজার বছর আগেও কেন যে বনে বা পাহাড়ে আসতেন তাঁদের বোধির জন্যে, জীবনের মানে খোঁজার জন্যে, দিক ঠিক করার জন্যে, এমন পরিবেশে
এলে বেশ কিছুদিন না থাকলে বোঝা পর্যন্ত যায় না। আধ্যাত্মিকতাইএল, আত্ম-নির্ভরতাই এল, আর আত্মার স্বরূপ, নিজস্বতার স্বরূপ আবিষ্কার ও যথার্থরূপে তাকে অনুভব ও উপলব্ধির কথাই এল, এমন নির্জনে না এলে তা বোঝা আদৌ সম্ভব নয়। কীসের জোরে যে, তোমার বেলায় যা করতে পারিনি, তা হনসোর বেলাতে অতিসহজেই করতে পারলাম সেকথা তুমি এখানে এসে যদি কটা দিনও কাটিয়ে যাও তাহলেই বুঝতে পারবে। হনসো তো তোমার চেয়েও অনেকই বেশি বিজাতীয় আমার কাছে। তোমার সঙ্গে আমার মন ও শরীর অনেক সহজে সবকিছুই চালাচালি করতে পারত। শিক্ষা ভাষা রুচি এবং মানসিকতার মিলও ছিল। সমতা ছিল অনেকই বেশি, অনেকই ব্যাপারে। শরীরে এবং মনে আমরা আদর্শ দম্পতি হতে পারতাম। পরীক্ষা-নিরীক্ষা তো তাই-ই প্রমাণ করেছিল। কিন্তু তবুও আমরা হইনি। তুমি পারোনি ইংল্যাণ্ড ছাড়তে, আমি পারিনি দেশ ছেড়ে থাকার কথা ভাবতে। কিন্তু পাহাড়-অরণ্যের কোনো দেশভেদ নেই। জাত মানে না সে। মানুষের, সব দেশের সব কালের বিশ্বমানবের মুক্তি নিয়ে সে কোটি কোটি বছর ধরে বসে আছে আমাদেরই আসার প্রতীক্ষায়। তুমি এলে না, তাই পেলে না।
রবীন্দ্রনাথের সেই গানেরই মতো যেন বিশ্বমানবকে নীরবে ডাক দিয়ে বলছে এই প্রকৃতি : বাহির পথে বিবাগী হিয়া কীসের খোঁজে গেলি, আয়, আয় রে ফিরে আয়। পুরানো ঘরে দুয়ার দিয়া ছেঁড়া আসন মেলি বসিবি নিরালায়, আয়, আয় রে ফিরে আয়।
মার্গারেট, লক্ষ্মীমেয়ে, তুমি একা অথবা যদি বিয়ে করো, তোমার স্বামীসমেত এখানে বেড়িয়ে যেয়ো অবশ্যই একবার। যদি আসো তবে তুমি শুধু আমার দেশকে নয়, শাশ্বত পৃথিবীকে, যুগযুগান্ত ধরে বিশ্বমানবের প্রার্থিত প্রকৃত ধনকেই হৃদয়ে অনুভব করবে। এই প্রেম আমার তোমার প্রেমের চেয়ে অনেক বড়ো, অনেক, অনেকই বড়ো, সমস্ত প্রেমের নরম পরিপুতি এরই মধ্যে।
শিকার আমি নিজে ছেড়ে দিয়েছি একেবারেই। হনসোদের আনুষ্ঠানিক যেসব বিশেষ শিকার-যাত্ৰা হয়, বিশেষ বিশেষ পরবের দিনে, তাতে অবশ্য যোগ দিই। তবে তির-ধনুক নিয়েই। কিন্তু তুমি বা তোমার স্বামী শিকার করতে চাইলে আমার আপত্তি নেই।
অন্যেরা যখন শুটিং ব্লক রিজার্ভ করে বন-বাংলোতে থেকে শিকার করতে পারেন তোমরাও তেমনি পারবে যদি চাও। সব বন্দোবস্তই আমি করে দেব। কিন্তু আমি তাতে অংশ নেব না। বিশ্বাস করো, শিশুকাল থেকে শিকার করছি, শিকারে নিরাসক্তি এসেছে। পরমভোগের পর যে নিরাসক্তি আসে সেইটেই প্রকৃত নিরাসক্তি। জীবনের সবক্ষেত্রেই বোধ হয় একথা প্রযোজ্য। আমি প্রায় নিশ্চিত এ ব্যাপারে। যতক্ষণ ভোগ না পুরো হয় ততদিন নির্লিপ্তি কাকে যে বলে তার ধারণা পর্যন্ত করা যায় না।
শুনে হয়তো অবাক হচ্ছ তুমি যে, এসব বিশেষ পরবের দিনেও আমি তির-ধনুক বা বল্লম নিয়েই শিকার করতে যাই। এখন আমার মনে হয়, আধুনিক বন্দুক রাইফেল, অনেক আধুনিক যন্ত্রাতিরই মতো, মানুষের মনুষ্যত্ব, মানুষের পার্সোনাল শিভালরি নষ্ট করে দিয়েছে। কন্টিনেন্টে হলিডেতে গিয়ে স্পেনের আলটামিরার গুহাগুলিতে আমরা যেমন ছবি দেখেছিলাম প্রাগৈতিহাসিক মানুষদের আঁকা, তাতে পাথরের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে অতিকায় সব পশুদের মোকাবিলার দৃশ্যই তো আঁকা ছিল। কী? ছিল না? আমাদের এই আধুনিক বিজ্ঞান, বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ এই আমরা বিজ্ঞানকে যতই বড়ো করে তুলেছি এবং তুলছি, অবশ্যম্ভাবী, অপ্রতিরোধ্য সর্বগ্রাসীই হচ্ছে তার প্রভাব আমাদের ওপরে। মানুষ হিসেবে আমরা ততই ছোছাটো হয়ে যাচ্ছি, দুর্বল হয়ে যাচ্ছি, প্রতিনিয়ত শারীরিক ও মানসিকভাবে। অ্যারিথমেটিক্যাল প্রোগ্রেসানে আমরা ছোটো হচ্ছি, কিন্তু এক শ্লাঘা সম্পূর্ণ বৈপরীত্যে জিয়োমট্রিক প্রোগ্রেসানে আমাদের মাথার মধ্যে গ্যালপিং গ্রোথের টিউমারের মতোই বড়ো হচ্ছে। এই শ্লাঘার টিউমার শিগগিরই আমাদের মতো আধুনিক বিজ্ঞানসর্বস্ব মানুষদের মস্তিষ্ক দীর্ণ করে দেবে বলেই আমার বিশ্বাস। মানুষের অনেক ক্ষমতাসম্পন্ন মস্তিষ্কের বদলে, যেসব ক্ষমতার পূর্ণ মূল্যায়ন পর্যন্ত হয়নি এখনও, প্রোগ্রাম ঠাসা কম্পিউটারে মানুষ তার নিজস্বতাকে সম্পূর্ণ নির্মূল করে দেবে। মানুষের মতো এমন মূর্খ, দাম্ভিক, অপরিণামদর্শী জানোয়ার বিধাতা আর গড়েনইনি।
বাট্রাণ্ড রাসেল, তাঁর ইন প্রেইজ অফ আয়লনেস বইতে বড়ো সরল উৎসাহ এবং সৎ উদ্দীপনার সঙ্গে বলেছিলেন, যে যন্ত্র আবিষ্কার হওয়ার পর ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের পর, যন্ত্রে ওপরে পৌনঃপুনিকতার বোঝা চাপিয়ে দিয়ে মানুষ তার মস্তিষ্ককে মানবিক ক্রিয়াকান্ডে লাগাতে পারবে। কুঁড়েমি মানুষের উদ্ভাবনী-শক্তি, কল্পনাশক্তি এবং অন্যান্য মানবিক গুণের বিকাশ নিশ্চয়ই করে। তাই কুঁড়েমির প্রশস্তি করেছিলেন তিনি।
কত বছর আগে তিনি ওই কথা বলেছিলেন! অথচ দেখো, আজকে ঠিক তার উলটোটাই হল। কোথায় যে চলেছি আমরা, এই তথাকথিত জ্ঞান-ঋদ্ধ, সর্বজ্ঞ আধুনিক মানুষেরা তা বোঝার ক্ষমতাও বোধ হয় হারিয়ে ফেলেছি।
শিকার করি অথচ বন্দুক-রাইফেল সঙ্গে নিই না যে কেন তার পেছনে আমার নিজস্ব যুক্তি আরও আছে। আর্নেস্ট হেমিংওয়ের দ্য ওল্ড ম্যান অ্যাণ্ড দ্য সীতে হেমিংওয়ে এই ব্যাপারটার চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ব্যাখ্যা হিসেবে নয়। তাঁর দীর্ঘদিনের পাহাড়-জঙ্গল সমুদ্রর অভিজ্ঞতা থেকে যা তিনি শিখেছিলেন তাই-ই ব্যক্ত করেছেন তাঁর সৃষ্ট চরিত্রর মাধ্যমে।
দ্য ওল্ড ম্যান এণ্ড দ্য সী-র বুড়ো সান্টিয়াগোর চরিত্রটির কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে কোনোই ঝগড়া ছিল না। সান্টিয়োগোর মনোভাব, অ্যাটিচ্যুড ছিল সমর্পণের; রেজিগনেশন-এর। সান্টিয়াগো সমুদ্রের প্রমত্ততাতে তার প্রতিদ্বন্দ্বী সেই অতিকায় মাছটির কাছে হেরে যাবে যে, একথা যেন মেনে নিয়েই তার ছোটো ডিঙি নিয়ে সেই মাছটির সঙ্গে টক্কর দিতে যেত। সমুদ্রের স্বগতোক্তি শুনতে শুনতে সে খুঁজে বেড়াত।
কাকে?
তার প্রতিদ্বন্দ্বী মাছটিকে?
নাকি নিজেকেই?
প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধে নোনা-গন্ধ আদিগন্ত জলরাশির মধ্যে ছোটো ডিঙিতে ভাসমান থেকে সী-গাল আর টার্নদের বিধুর আধিভৌতিক চিৎকারে প্রকৃতির বিরাটত্বকে না মেনে যে উপায়ও নেই কোনো মানুষের। সেই বুড়োর মস্তিষ্কে একমুহূর্তের জন্যেও এমন ভাবনা আসেনি যে, তার অনুষঙ্গ, তার পরিবেশের তুলনায় সে নিজে কোনো অংশেই বড়ো। এমনকী সান্টিয়াগো নিজেকে তার প্রতিদ্বন্দ্বী সেই মাছটি থেকেও বড়ো বলে কখনো মনে করেনি। মাছটিকে সে বরাবর ব্রাদার বলে সম্বোধন করেছে। সেই মাছটিকে সান্টিয়াগো একদিন ধরতে পেরেছিল যদিও, তবুও তিলেকের জন্যেও মাছটি যে তার থেকে কোনো অংশে নিকৃষ্ট এমন ভাবনা তার মাথায় আসেনি।
তোমার মনে থাকতে পারে মার্গারেট, সান্টিয়াগো যেখানে বলছে, ম্যান ইজ নট মাচ বিসাইড দ্য গ্রেট বার্ডস অ্যাণ্ড বিস্টস।
যেসব সময়ে সান্টিয়াগো নিজেকে মাছটার চেয়ে বড়ো বলে উল্লেখ করেছে সেখানেও সে বলছে :আই অ্যাম ওনলি বেটার দ্যান হিম থু ট্রিকারি।
আমিও যে বাঘের চেয়ে বাইসনের চেয়ে, হাতি বা বুনোমোষের চেয়ে শক্তিশালী তার সবটাই থ্রু ট্রিকারি।
জীবনের একটা সময়ে পৌঁছে ট্রিকারি মাত্রকেই মকারি বলে মনে হয় হয়তো সকলেরই। আমার যেমন হচ্ছে। মার্গারেট, একদিন সমস্ত পৃথিবী জানতে পাবে যে, মানুষের এই শ্লাঘা, এই বিজ্ঞানসর্বস্ব, আরাম ও বিলাস-সর্বস্ব কতৃত্ব অন্য সব প্রাণী এবং প্রকৃতিরও ওপরে, এই সবই ঞ ট্ৰিকারি।
জানি না, তুমি হয়তো আমার চিঠি পড়ে হাসছ। যেমন করে তুমি বলতে আমাকে হাইড পার্কের প্রাচীন গাছের ছায়ায় পার্কের বেঞ্চে বসে আমার কাঁধে হাত রেখে, তেমন করেই : আ রিয়্যাল ম্যাড়ক্যাপ। তোমার দুই ঠোঁটের কোনায় আর গালে সেই স্নিগ্ধ হাসির আভাস ফুটে উঠেছে নিশ্চয়ই। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।
মার্গারেট, আমি যাই-ই তোমাকে লিখি না কেন, তা যত্ন করে কোনো ভল্টে রেখে দিয়ো। যা বলছি তাতে হেসো না একটুও।
সত্যদ্রষ্টাদের কথা তার সমসাময়িক কোনো মানুষই বুঝতে পারে না। তারা চিরদিনেরই পাগল। প্লাটো, সক্রেটিস, স্পিনোজা, কনফুসিয়াস, টলস্টয়, রাসেল–তাঁদের সকলেরই জীবনের কোনো-না-কোনো সময়ে টিটকিরি, গালমন্দ, ইটপাটকেল অথবা বিষ জুটেছিল। তাই বলে তাঁদের বলে-যাওয়া-কথা কিছু মিথ্যে হয়নি। যাঁরা অনেক দূরে এগিয়ে গিয়ে ভাবেন, তাঁদের ভাবনার কথা বুঝতে পারা তাঁদের সময়ের সাধারণ মানুষদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। কোনোদিনও সম্ভব হয়নি। আমাকে দাম্ভিক ভেবো না। আমি শুধু অন্যরকম, অন্য কালের; সর্বদেশের। আমি বিশ্বমানবের প্রকৃত মুক্তির কথাই বলছি বার বার। তোমরা না বুঝলে ক্ষতি তোমাদেরই। যখন বুঝবে তখন আমি থাকব না। ভবিষ্যতের পৃথিবীর মানুষেরা আমার কথার তাৎপর্য বুঝতে পেরে দেশে দেশে আমার মূর্তি গড়বে। এই পরিহাস প্রত্যেক দূরদ্রষ্টার ঠিকুজি। সমসময়ের হাতে এই নিগ্রহ, সমসাময়িকদের চোখে এই তুচ্ছতা, ঘৃণা। জীবনে তারা শুধু অপমান আর অসম্মানই পায়।
মার্গারেট! কে বলতে পারে যে, তোমার নাতিরা অথবা পুতিরা তোমার সঙ্গে আমার কোনো সময়ে যে প্রেমের সম্পর্ক ছিল এই নিয়ে গর্বিত হবে না? তোমাকে লেখা আমার এই চিঠিগুলির একটি বিক্রি করেও তারা কোটিপতি হবে না?
হেসো না সুইটি পাই। হেসো না। ভবিষ্যৎ যে বর্তমানের কোন ধূলিকণার মধ্যে নিহিত, সুপ্ত থাকে, তা কে জানে? ভবিষ্যতের কথা শুধুমাত্র ভবিষ্যৎ-ই জানে। তবে মার্গারেট, যদি এখানে তুমি একবার আসো, এসে আমার এই সার্বিক পরিবর্তনটা দেখে যাও, তবে খুবই ভালো লাগবে আমার।
.
যেদিন মার্গারেট আমাকে হিথ্রো এয়াপোর্টে তুলে দিতে এসেছিল সেদিন মনে খুবই কষ্ট হয়েছিল। ওর মতো মেয়েকে স্ত্রী হিসেবে পাওয়ার সব সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও তাকে ছেড়ে চলে আসতে ভেতরে জোরও কম লাগেনি। কষ্ট হয়তো ওরও কম হয়নি। কিন্তু কেন জানি না, এখন মনে হয় বিয়ে হয়নি বলেই আমাদের দুজনের মধ্যের এই ভালোবাসার সম্পর্কটি চিরদিনই থেকে যাবে। যখনই একে-অন্যকে প্রয়োজন হবে, দুজনে দুজনকে কাছে পাব আমরা। মনের কাছে। ভালোবাসাতে শরীরের ভূমিকা আর কতটুকু? মন-ই তো আসল। ভালো যে বাসতে জানে, সে-ই একথা জানে।
বিবাহিত জীবন হচ্ছে ক্যাকটাস আর বিবাহ-বন্ধনহীন প্রেম হচ্ছে মৌসুমি ফুল। নরম, চোখ-জুড়োনো রঙের; যদিও প্রায়শ-গন্ধহীন।
.
০৬.
গ্রাষ্মের রাতগুলি ভারি সুন্দর। রাতের কথা শুধু রাতের বেলাতেই বলা চলে। এমন অনেক ভাবনা আছে যা দিনের বেলা ভাবাই যায় না।
রাতেরও কতরকম আছে। মিথ্যে রাত, সত্যি রাত, তরল রাত, বর্ষার রাত, অন্ধকার রাত, চাঁদের রাত। এতরকমের রাত, অথচ প্রত্যেক রাতের সৌন্দর্যই আলাদা আলাদা। ভাবনাই আলাদা আলাদা। তাদের বক্তব্য, ভাষাও তাই।
এমন এমন রাতে আমি একা একা জঙ্গলে ঘুরে বেড়াই। হনসো ভয় পায় বলে, সাপ আছে। নানারকম দানো এবং প্রেত আছে। জিন-পরিরা আছে।
সত্যিই এসব আছে কি না জানি না। সাপ-বিছে বাঘ-বাইসন অবশ্য আছেই। বনের রাতের মধ্যে কী যে আছে আর কী যে নেই তা আমি কেন প্রায় কেউই জানে না।
শিক্ষিত, শহুরে মানুষেরা হয়তো বলবেন–আলো নেই, পিচ-রাস্তা নেই, নানারকম জন্তু জানোয়ার, তাই রাতের বেলা বনে-জঙ্গলে কেউ ঘরের বাইরে বেরোয় না। কিন্তু শুধু এইসবই নয়। কারণ আরও আছে।
লক্ষ করেছিলাম আগেও যখন শিকারে আসতাম, এবং এখন তো করছিই যে, বন-জঙ্গল এবং বন-জঙ্গলের কাছাকাছি সমস্ত এলাকাতেই অলিখিত সান্ধ্য-আইন জারি করা আছে। সূর্যের সঙ্গেই সকলের জীবন বাঁধা। যে জঙ্গলে হিংস্র জানোয়ার একেবারেই নেই সেখানেও জংলি মানুষেরা সন্ধের পর বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া ঘরের বাইরে বেরোয় না। এই ভয় সংস্কারজাত? না এর পেছনে অন্য কিছু আছে, তা খুব জানতে ইচ্ছে করে।
যেসব মুণ্ডা যুবক দিনের বেলা তির-ধনুক হাতে যমের গুহার মধ্যে ঢুকে যেতেও পিছপা হয় না তারাই রাত নামলেই কেঁচো।
জানি না, আমি এখানে থাকতে থাকতেই হয়তো এই শালডুংরিতেও বিজলি আলো এসে যাবে। তখন হয়তো রাতে আর দিনে তফাতই থাকবে না কোনো। কলকাতা বা লানডানেরই মতো। কিন্তু সেই শালডুংরি কি এই শালডুংরি থাকবে?
এই রাতের টহলে মনের মধ্যে নানা কথা ওঠে। অন্ধকার পাহাড়তলির ঘন জঙ্গলের মধ্যে পায়ের তলায় শুকনো পাতা মচমচিয়ে ভেঙে অন্ধকারতর কোনো জানোয়ার আমাকে চমকে দিয়ে ছুটে চলে যায়। আড়াল থেকে আমাকে দেখে। কখনো তারার আলোর আভাতে জানোয়ারদের ভূতুড়ে চোখ ঝলসে ওঠে একলহমার জন্যে। দুঃস্বপ্নে দেখা আবাস্তব ভয়ংকর জন্তুর চোখেরই মতো। মাংসাশীদের চোখ লালচে দেখায়। আর তৃণভোজীদের সবজে। সাধারণত।
প্রথম প্রথম ভয় পেতাম। ভয়ের বাসাই যে অজ্ঞানতার বুকের কোরকে। যেখানে জানার শেষ, সেখানেই ভয়ের শুরু। এখন অনেকই রাতে একা একা ঘুরে ঘুরে জানোয়ারদের চেহারা না দেখেও শুধুমাত্র আওয়াজ শুনেই মোটামুটি বলতে পারি কোন জানোয়ার। মাঝে মাঝে আকাশ এবং আকাশের তারাদের আড়াল করে পথের ওপরে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে পাহাড়ের মতো অনড় হাতিরা। তারা সরে গেলেই আবার তারা ফোটে।
কেন জানি না, এই নির্জন, ভাবগম্ভীর পরমা প্রকৃতি, আমার এবং সব মানুষের প্রকৃত মা, আসল প্রেমিকা, আমার মধ্যে কেবলই ঈশ্বরবোধের ব্যাপারটাকে নাড়া দেন। ভোগবিলাসের দফা-রফা তো নিজের হাতেই করলাম। আমার বয়েসি যুবকের এমন আরণ্যক জীবন বরণ করা, প্রাকৃত নারীকে বিয়ে করা এসবই তো অন্য দেশ হলে খবরের মতো খবর হত। রিপোর্টাররা, ফোটোগ্রাফাররা আর টিভির মানুষেরা মেলা বসিয়ে দিত এখানে। এই জীবন বেছে নেওয়াটাই যথেষ্ট বিস্ময়ের ব্যাপার। আমার নিজেরও কাছে।
মাঝে মাঝেই মাটির দেওয়ালে কাঠের খোঁটাতে টানানো হাট থেকে-কেনা হলুদ-কাঠের ফ্রেমের মধ্যে বসানো লাল-পারা-লাগানো সস্তার আয়নাতে নিজের মুখ দেখি। আর ভাবি, সেই আমিই তো? সেই আমিই কি?
কিন্তু এই বয়েসেই আমার মতো একজন বিলেত-ফেরত নব্য-যুবকের মনে ঈশ্বরবোধ জন্মনো কি সুস্থতার লক্ষণ? আগে তো জানতাম অনেক পাপটাপ করার পরেই পাপ শোধনের জন্যে বৃদ্ধ বয়েসের জড়ি-বুটি এই ঈশ্বর-বোধ। তাই-ই তো জেনে এসেছিলাম এতদিন। ভাবতাম, ঈশ্বর বা গুরু এসব তো নীচুস্তরের মানসিকতার বা জড়বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ অথবা গ্রামের মেয়েদের-ই জন্যে। আমার কমিউনিস্ট বন্ধুরা তো তাই বলেন গলার শিরা ফুলিয়ে। কমিউনিস্টদের সঙ্গে ঝগড়া করে কখনো জেতা যায় না বরং গলায় গার্গল করতে হয় রাতে। হয়ই! শুধুমাত্র গলার জোরেই এমন দেশসেবার কথা ভাবা পর্যন্ত যায় না! তাই কমিউনিজম, বিজ্ঞানের জগৎ আর ঈশ্বর কখনো সহাবস্থান করতে পারেন না। এই কথাতেই বিশ্বাস করতাম।
কিন্তু এখানে এসে সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে গেল! আজকাল আমি যেন কার অদৃশ্য অস্তিত্ব অনুভব করতে পারি। আকাশ হতে হঠাৎ খসে-যাওয়া তারার উজ্জ্বল সবুজ ক্ৰম বিলীয়মান রেখাঁটিকে ক্ষণিকের মধ্যেই অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখে অবাক হয়ে ভাবি যে, খসে যাওয়া তারাটি আমাদের এই পৃথিবী থেকে কত কোটি গুণ বড়ো ছিল? কত কোটি আলোক-বর্ষ দূরে ছিল তা কে জানে? কে এই অগণ্য গ্রহ-নক্ষত্রকে ধরে রেখেছেন? কার অঙ্গুলিহেলনে এই ব্রহ্মান্ডের ক্রিয়াকর্ম চালিত হচ্ছে? বিজ্ঞান তো অনেকই জেনেছে। কিন্তু সেইসবই তো নিছক আবিষ্কারই। সব তো ছিলই। উদ্ভাবন কী করেছে বিজ্ঞান? কী? যা কিছুই ছিল, সেইসব কিছুকেই তার জিজ্ঞাসা, তার জিগীষা, তার অদম্য অনুসন্ধিৎসার আলো ফেলে চিরে চিরে দেখেছে, প্রতিমুহূর্তে দেখছে মানুষ। এইমাত্র। যা-কিছুই ছিল, আছে, সেইসমস্ত বস্তুর শবব্যবচ্ছেদে কোনোরকম ত্রুটিই নেই। জীবন? জীবন কি তৈরি করতে পারবে মানুষ?
কোনোদিন হয়তো টেস্ট-টিউবে বেবি হবে। কোথাও কোথাও হচ্ছেও। কিন্তু তা জীবনের বিকল্প নিশ্চয়ই নয়। কী করে কী হয়, তা তো অনেকই জানলাম কিন্তু কে যে করান এসব তা জানা হল কই? অতলান্ত সমুদ্রের গহন ঘনকৃষ্ণতলে যে হাইওয়ে আছে, আছে। এসকালেটর যাতে একবার গিয়ে পৌঁছোত পারলে দুর্বার গতিতে হাজার হাজার মাইল পেরিয়ে গিয়ে ভিন-সমুদ্রের মাছেরা পৌঁছোয় নিমেষে এক সমুদ্র থেকে অন্য সমুদ্রে, পৌঁছে যায় অতলান্ত থেকে উচ্চতায় তো আমরা জানিই! কিন্তু কে এইসব বানিয়ে রেখেছেন? একরত্তি পাখি বা একচিলতে প্রজাপতির মধ্যে কে এত গান গিয়েছেন? জীবন এবং মৃত্যুর বিচিত্র নিয়ম-কানুন লক্ষ লক্ষ রকম পশু-পাখি পোকামাকড় মাছ সরীসৃপের জন্যে আলাদা করে বানিয়েছেন কে?
কে তিনি?
তিনিই কি বিজ্ঞান? নাকি?
আমার বোধ হয় মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটে যাচ্ছে। অথবা ইতিমধ্যেই গেছে। এরপরে সভ্যজগতে আমাকে আর ফিরিয়ে নেবে না কেউই। এই স্বেচ্ছা-নির্বাসনই আমার সমস্ত অধীত-বিদ্যা, অঢেল অর্থব্যয় অর্জিত তাবৎ জ্ঞান এবং অন্য সমস্ত কিছু প্রাপ্তিকেই মাটি করে আমাকে হাত ধরে পেছনে নিয়ে গিয়ে একেবারে স্টার্টিং-পয়েন্টে পৌঁছে দিল। আধুনিক, আলোকপ্রাপ্ত, একজন যুবক, প্রাগৈতিহাসিক, অন্ধকারাচ্ছন্ন জঙ্গলের আদিবাসী মানুষ বনে গেলাম।
সংস্কারাচ্ছন্নও কি?
আমার মুক্তি নেই আর।
সেদিন কলকাতায় একজনের কাছে বিখ্যাত শিল্পী বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের লেখা ক টি চিঠি পড়ছিলাম। চিঠিগুলো হয়তো কখনো ছাপাও হবে। আরণ্যক এই সম্বোধন করে লেখা। আরণ্যক যে কে, তা রহস্যই থাক। বিনোদবিহারীও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন যে, কোনোদিনও তা প্রকাশ করবেন না। এই প্রচারের যুগে এমন আড়ালে থাকতে চাওয়া মানুষেরাও বড়ো বিরল হয়ে যাচ্ছেন।
উনি লিখছেন :
আপনার সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছে আমারও হয়। তাতে কিছুক্ষণের আনন্দ নিশ্চয়ই হবে কিন্তু মনের যে গভীর শূন্যতা আপনি ও আমি অনুভব করছি, সেই শূন্যতা আবার ফিরে আসবে।
কিছুদিন আগেই চিঠিগুলি পড়ছিলুম। চিঠির শেষ অংশে লেখা আছে :
তুমি যুক্তিবাদী, বুদ্ধিমান। কিন্তু একথাও জানবে ঈশ্বর ছাড়া উপায় নেই। ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ করার চেষ্টা করবে। ভারতবর্ষর সাধকরা বহু পথ দেখিয়ে গেছেন। ধ্যান, কর্ম, ভক্তি এই তিন মূলসত্য থেকে নিজের পথ খুঁজে নিতে হয়।
কিন্তু পথ খোঁজবার শক্তি কোথায়? আপনি কি সেই শক্তি পেয়েছেন?
অন্য চিঠিতে লিখছেন :
যাঁরা আমাদের চেয়ে সকল বিষয়ে বড়ো, তাঁরা সকলেই ঈশ্বর এবং মঙ্গল এক করে উপলব্ধি করেছেন। আমাদের মতো সাধারণ মানুষ মেন্টাল-ওয়ার্ল্ড-এর গন্ডির বাইরে প্রায়ই যেতে পারে না। (এ বিষয়ে আমি ছবি আঁকতে গিয়ে বুঝেছি।)
একস্ট্রিম মেন্টাল-শক, লাঞ্ছনা, অপমান, কাম ইত্যাদির প্রভাবে আমাদের মনে যে, একরকম বৈরাগ্য ভাব জন্মে বা তীব্রভাবে আমরা কোনো কোনো বিষয়বস্তুতে আকৃষ্ট হই, তখন একরকমের মুক্তি অনুভব করি। সৃষ্টিক্ষমতা যদি না থাকে তাহলে এই অবস্থা থেকেই আমরা একটা অন্ধকার জগতে গিয়ে পৌঁছোই (মানসিক নরক)। অলৌকিক অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই আছে। আসলে নির্জনবাস ও জনতার মধ্যে বাস করার মধ্যে অভিজ্ঞতার পথে জমিন-আসমান তফাত রাখে (আপনি ঠিকই লিখেছিলেন, নির্জনতা কখনো আমাদের শূন্যহাতে ফেরায় না)।
লেখাপড়া, ছবি আঁকা সবই নির্জনতার অবদান। বাইরে নির্জনতা থাকলেও মনের মধ্যে ভিড় জমে ওঠে। বাইরেও নির্জন, মনের ভেতরেও নির্জন–একেই বোধ হয় শান্তি বলে।…এরপরই ঈশ্বর আছেন না নেই, সৌন্দর্য আছে না নেই এ সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন থাকতে পারে। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে, সর্বশক্তিমান আমাদের ভালোমন্দর হর্তাকর্তা ভগবানকে আমি দেখিওনি, বুঝিওনি। আমি অলৌকিকে বিশ্বাস করি। অপ্রত্যাশিতভাবে মানুষের মনের পরিবর্তন ঘটে। যুক্তির পথ উপলব্ধির পথ দুটি ভিন্ন। যুক্তির পথে ছবি আঁকতে পারিনি। ছবি আঁকার জন্যেই উপলব্ধির পথ অনুসরণ করতে হয়েছে।
একলা এসেছি এ ভবে
একা যেতে হবে চলে…
এই ছড়াটি আজকাল খুব মনে পড়ে। অজানা পথে একা চলবার জন্যে প্রস্তুত হয়েছি, এবং সেই পথেই দিনে দিনে, ঘণ্টায় ঘণ্টায় এগোচ্ছি। পথের শেষে কার সঙ্গে দেখা হবে। ঈশ্বর? নিয়তি? না অসীম শূন্যতা?
অন্য একটি চিঠিতে বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় আরণ্যককে লিখছেন :
তলায় পাঁক, মাঝখানে জল, ওপরে পানা এই হল মোটামুটি আমাদের জীবন। কোনো রকম করে পানা সরাতে পারলে একটু সূর্যের আলোক পড়ে, সেই হল ঈশ্বরের আশীর্বাদ। পাহাড়, সমুদ্র, তারায় ভরা অন্ধকার রাতের কথা মনে হলে পানা পুকুর থেকে মুক্তি পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা জাগে। মুক্তি হয়ত হবে না, তবু বৃদ্ধ বয়সের পরম সম্পদ এই অভিজ্ঞতা; যা আমাদের মুহূর্তে মুহূর্তে জানিয়ে দিচ্ছে যে আরও কিছু আছে। যৌবন হল অ্যাকশন আর বার্ধক্য হল কনটেমপ্লেশন। এই সত্যটি জানতে অনেকদিন লাগল।
এই চিঠিগুলি পড়েও আমি কম বিপদে পড়িনি। বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের মতো ক্ষণজন্মা শিল্পীর মতে যখন অ্যাকশন-এর সময় তখই আমি কনটেমপ্লেশন-এর দিকে ঝুঁকেছি। এও বোধ হয় আমার অকালপক্কতার আর এক দিক।
কাউকে বুঝিয়ে বলতেও পারি না। বললে কেউ বিশ্বাসও করবেন না। একলা বনপথে হাঁটতে হাঁটতে আমি যেন কারো করতলের ছোঁয়া অনুভব করি আমার মাথার ওপরে।
কার ছোঁয়া? আমার পরলোকগতা মায়ের?…
নাকি..
.
০৭.
ঈশ্বরবোধের, ভালোবাসার, নানারকম আছে। ইংল্যাণ্ডে থাকাকালীন আমার সঙ্গে মার্গারেটের এককরম ভালোবাসা ছিল। সে ভালোবাসা এখন অন্যরকম হয়েছে। আবার হনসোর সঙ্গে একরকমের ভালোবাসা। আমার সদ্য-স্ফুটিত ঈশ্বর-বোধও অন্য এক ধরনের ভালোবাসাই!
মনে হয়, অধিকাংশ ভালোবাসাই বোধ হয় কিছু না কিছু চায়ই বদলে। যে-ভালোবাসা কিছুই চায় না, বদলে কেবল দিতেই চায়, তাই-ই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ ভালোবাসা।
সাম্প্রতিক অতীতে মার্টিন লুথার কিং এই ব্যাপারটাকে সুন্দর করে প্রকাশ করেছেন। ভালোবাসাকে উনি তিনরকমভাবে ভাগ করেছিলেন। ওঁর সম্বন্ধে মিসেস কোরেটা কিং-এর লেখা একটি বইতে এ কথা পড়লাম। এর তিনটি ভাগ ছিল এইরকম।
১। EROS : দ্য সোওলস ইয়ার্নিং ফর দ্য ডেজায়ার, দ্য এস্থেটিক, অর রোমান্টিক
২। PHILIA: রেসিপ্রোকাল লাভ
৩। AGAPE : ডিস্ট্রিংট লাভ, নট ফর ওয়ানস ওওন গুড বাট ফর দ্য গুড অফ ওয়ানস ওওন নেবার, নট উঈক অর প্যাসিভ বাট লাভ ইন অ্যাকশান।
এই AGAPE থিমটি মার্টিন লুথার কিং তাঁর আত্মজীবনীমূলক বই পিলগ্রিমেজ টু নন ভায়োলেন্স-এ পল্লবিত করেছেন খুবই ভালো করে।
আরও একটি বই পড়লাম, ওঁর-ই লেখা–স্ট্রেংথ অফ লাভ। থ্রি ডায়মেনশানস অফ কমপ্লিট লাইফ-এ উনি তিনরকমের ভালোবাসা অথবা চিন্তার কথা বলেছেন। প্রথমত নিজের ভালোর চিন্তা, দ্বিতীয়ত অন্যদের ভালোর চিন্তা, তৃতীয়ত কনসার্ন ফর দ্যাট ইটার্নাল বিয়িং হু ইজ দ্য সোর্স অর গ্রাউণ্ড অফ ওল রিয়ালিটি।
মার্টিন লুথার কিং-এর বড়ো উদবেগ ছিল তাঁদের জন্যে : ফর দোজ হু লিভ অ্যাজ দো দেয়ার ইজ নো গড।
উনি বার বারই সেই হতভাগ্য সব মানুষদের মনে করিয়ে দিয়েছেন, যাঁরা চিরদিন ম্যান সেন্টারড পৃথিবীতেই বাস করেন, তাঁর নিজস্ব ওজস্বী ভাষাতে তিনি তাঁদেরই উদ্দেশে
বলেছেন :
You can never see the me that makes me me, And I can never see the you that makes you you. That invisible something we call personality is beyond our physical gaze.
যাঁরা আমাদের চেয়ে সকল বিষয়ে বড়ো তাঁরা সকলেই ঈশ্বর এবং মঙ্গল এক করে উপলব্ধি করেছেন। বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় ঠিক এই কথাই, মানে কিং-এর কথাই বলেছিলেন।
বড়ো বড়ো মানুষদের লেখা বই পড়ে এবং কথা শুনে আমার মন কেবলই বলে : কেউ নিশ্চয়ই আছেন, যিনি এই অসীম ব্রহ্মান্ডকে ধরে রেখেছেন, এই কোটি কোটি নক্ষত্র-নিচয়কে পরিচালন করছেন। শালডুংরিতে না এলে, না থাকলে এই কথা হয়তো কোনোদিন উপলব্ধি করতেই পারতাম না।
নির্জনতা সত্যিই কখনো আমাদের শূন্যহাতে ফেরায় না।
আমিও এই কথা হৃদয়ংগম করতে আরম্ভ করেছি।
আমি জানি, আমার বন্ধুরা, আত্মীয়স্বজনেরা আমাকে মূর্খ অথবা পাগল বলবেন কিন্তু আমি নিরুপায়। মনে যা হয় তাই-ই বলি, লিখি।
ডাইরিতে তো কোনো মানুষ মিথ্যে লেখে না!
আমার কমিউনিস্ট বন্ধুরা আমার নামে ছড়া কাটবেন জানি। কিন্তু খাদ্য-বস্তুর সংস্থান করার, নিপীড়িত জনগণের জাগতিক ভালোর চেষ্টা করার পরও ভালো করার বাকি আরও কিছু থেকে যায় মানুষ ইঁদুর বা কুকুর নয় বলেই। মানুষ মানুষ বলে। আমার কমিউনিস্ট বন্ধুরা সেকথা স্বীকার করুন আর নাই করুন।
বিন্দিয়া নদীর মধ্যে একটি দহ-মতো আছে, আমাদের কুঁড়ে থেকে দু-মাইল মতো দূরে। ঠিক সেখানেই বাঁকও নিয়েছে নদীটা। বৈশাখের প্রথমেই তাপ খর হয়েছে। নদীর জল কমে আসছে। দহটিতেও জল কমছে। কোনো সময়ে কোনো শিকারি মস্ত একটা মাচা বানিয়েছিল এই দহর ওপরে। কত বছর আগে তা কে জানে! তবে মাচাটি এমনই শক্ত যে, আরও বহু বছর অটুট থাকবে তা।
স্থানীয় লোকের মুখে শুনেছি ভোপালের নবাবদের কেউ কেউ এবং নবাব পতৌদিও একবার শিকারে এসেছিলেন। পতৌদিরা ভোপালের নবাবের জামাই। পতৌদির পরের প্রজন্মই টাইগার। মেয়ের ঘরের নাতি। ছেলেটি হয়তো কালে বড়ো ক্রিকেটার হবে। ইংল্যাণ্ডে নানা কাউন্টি ম্যাচে ওকে উৎসাহী দর্শক হিসেবে এবং কখনো কখনো খেলোয়াড় হিসেবেও দেখতে পেতাম। ক্রিকেটারের চোখ ছিল ছেলেটির। শিকারিদের পরিবারের ছেলের চোখের দৃষ্টি সচরাচর তীক্ষ্ণ ও ব্যাপ্ত হয়। ওর একটি চোখ ইংল্যাণ্ডেই মোটর দুর্ঘটনাতে নষ্ট হয়ে যায়।
নদীর ওপরে সেই মাচাটিতে কোনো কোনো দিন বিকেলে এসে বসি আমি। নানা বড়ো ছোটো জানোয়ার, মাংসাশী ও নিরামিষাশী, পাখি, প্রজাপতি এবং বিচিত্র-বৰ্ণর সাপেরা সব জল খেতে আসে বিকেলে। জল অবশ্য এখনও জঙ্গলের নানা জায়গাতে আছে। এই দহটি প্রায় দশ বর্গমাইলের মধ্যে একমাত্র জলের জায়গা হয়ে উঠবে আর মাসখানেক পর। জ্যৈষ্ঠ মাসে। তখন এখানে আসাই বিপজ্জনক হবে খালিহাতে শেষরাতে অথবা সন্ধের মুখে। হাতি, বাইসন, বুনো মোষ, বাঘ, বারাশিঙা, শম্বর, শজারু, চিতা, চিত্রল হরিণ, কৃষ্ণসার, কুটরা, খরগোশ, বুনো-কুকুর, শেয়াল, হায়না, বেজি, ময়ূর, মুরগি, তিতির, বটের এবং আরও অসংখ্য পাখি ও সাপে ও প্রজাপতিতে সরগরম হয়ে উঠবে এই জায়গা।
খালিহাতেই তো আসি। হাত এখন আমার সবদিক দিয়েই খালি। বন্দুক–রাইফেল, টাকাপয়সা, পরিচিতি, বল; কিছুই রাখিনি হাতে। এমনকী আমার সর্বক্ষণের সঙ্গী পাইপটি পর্যন্ত নয়। শূন্যহাতে না এলে যে, কিছু পাওয়াও যায় না। হাত শূন্য না থাকলে আজেবাজে অপ্রয়োজনীয় বস্তুতে ভরা থাকলে করপুটে তাঁর দান গ্রহণ করব কী করে? শূন্য হাতে ফিরি হে নাথ পথে পথে।
শূন্যতাই তো পূর্ণতার তীর্থপথের একমাত্র পাথেয়।
এইখানে এলে নানারকম জানোয়ার পাখি দেখলে, বনের এবং নদীর চরিত্রকে নিজের মধ্যে অনুভব করলে কত কীই যে স্বচ্ছ হয়ে ফুটে ওঠে চোখের সামনে কী বলব! ছোটো ছোটো পাখি আসে, তাদের ছোটো ছোটো ঠোঁটে করে জল খায়, ঘাড় পেছনে হেলিয়ে সেই জল গেলে, ছোট্ট গোল গোল উজ্জ্বল চোখে এস্ততার সঙ্গে তাকায়। সাপ আসে বুকে হেঁটে। বালির সঙ্গে শরীর মিলিয়ে জিভ বের করে জল খায়। সাপের খাদ্য পাখি, পাখির-ডিম, ইঁদুর, ছোটো ছোটো প্রাণী, পোকামাকড়। ময়ূরের খাদ্য সাপ। ময়ূর দেখলেই সাপ ভয়ে অদৃশ্য হয়ে যায় নিমেষে। চিতাবাঘ আবার ময়ূরের যম। বড়ো বাঘও ময়ূর খায়। ময়ূর ওদের দেখলেই কেঁয়া কেঁয়া করে বড়ো বড়ো ডাক ডাকে আর মস্ত ল্যাজ ঝটপটিয়ে ভারী শরীর নিয়ে মাটি ছেড়ে ওপরে ওঠে। চিতা আর বাঘের যম হল বুনো কুকুর। বুনো কুকুরের দল এলে তারা সেই জঙ্গল ছেড়ে পালিয়ে বাঁচে।
প্রকৃতির এই বৈচিত্র্যের মধ্যে এমন এক ধরনের ভারসাম্য দেখি যে, তা বলার নয়। যিনি জীব সৃষ্টি করেছেন তিনিই তাদের খাদ্য-সংস্থান করে পাঠিয়েছেন। সৃষ্টিতে একমাত্র মানুষের মতো ধূর্ত, লোভী, কান্ডজ্ঞানহীন জানোয়ার ছাড়া অন্য কোনো প্রাণীরই কোনো নালিশ নেই বিধাতার কাছে। বীভৎসতা, নিষ্ঠুরতা, রক্তারক্তি দেখে প্রাণীজগতে, বনজগতে যে বনের আইনতা প্রযোজ্য একথা আমরা আকছারই বলি। কিন্তু বনের আইন যে, শহরের আইনের চেয়ে অনেক ন্যায্য, অনেক উদার এ কথাটা বোঝার মতো সময় বা মানসিকতা বোধ হয় আমাদের নেই।
সাপে ব্যাং গেলে, বাঘে বারাশিঙা মেরে খায়, বুনো কুকুরে বাইসনের বাচ্চা বা হাতির বাচ্চাকে ছিঁড়ে খায় এসব চোখে দেখতে বীভৎস লাগে, কানে শুনলে মন বড়ো অশান্ত হয়। কিন্তু পরক্ষণেই যখন পুলকভরে পাখি ডেকে ওঠে, মৃদু হাওয়ায় পাতারা আন্দোলিত হয়, আলোছায়ার নিরন্তর খেলা চলে, বেলাশেষের শান্ত ছবি আর বিধূর ভাব বন থেকে উঠে এসে মনে পৌঁছোয়, মনের গভীরে সেঁধিয়ে যায়, তখন মনে হয় এমন তীর্থযাত্রা কি আর হয়! একজীবনে হেঁটে হেঁটে, ট্রেনে চড়ে, প্লেনে চড়ে ক-টি জায়গাতে আর যাওয়া যায়। মানসিকতায় যে প্রকৃত যাত্রী, যে যাত্রার মানে জানে তার চলা অবিরত। ভেতরে ভেতরে। আমাদের মনের মধ্যে যে এক বিরাট, আদি, অশেষ পৃথিবী, এতে ভ্রমণের আনন্দ যদি একবার আবিষ্কার করে মন, তাহলে তার সেই মনের তলায় সরষে নিয়ে সে অনুক্ষণই ঘুরে বেড়ায়। পায়ে পায়ে আর কতটুকু যাওয়া যায়। একশরীরে, একজীবনে! মনে মনে যাওয়াই তো আসল যাওয়া। মানুষের যাওয়া।
কিছু মানুষ আছে, মানুষের শরীরেই মানুষ, অতিস্থূল চরিত্রের মানুষ যাদের মধ্যে অনেকই অতৃপ্ত কামনা-বাসনা খিদে জমে আছে। তারা অনেক খাওয়া, অনেক ভোগ, অনেক দেশ দেখাকেই বাঁচার মতো বাঁচার সমার্থক বলে মনে করে। তাদের মনুষ্যত্ব আসলে সম্পূর্ণতা পায়নি। আরও অনেকবার ইঁদুর-বাদুড় হয়ে জন্মে তবে তাদের এই স্বচ্ছস্নিগ্ধ মানসিকতায় পৌঁছোতে হবে। অথচ এই কলিকালের রকম সকম এমনই যে ওই ধরনের লাঙুল-হীন হনুমানেরাই এই ধরাধাম দাপিয়ে হুম-হাম করে কাঁপিয়ে বেড়াচ্ছে অনুক্ষণ। এরা জানে না তাদের আসল ভাবের কথা, তাদের মানসিকতার প্রকৃত স্তরের কথা। তারা জানে না, জলের ওপরে শোলাই ভাসে, শিলা ভাসে না।
এই ধরনের মানুষদের প্রতি আমি এক ধরনের অনুকম্পা বোধ করি। প্রার্থনা করি, যেন তারা একদিন হৃদয়ে উপলব্ধি করে যে, যা কিছুই তারা ভ্রান্তির চরম বলে জেনে গেল যে ভ্রান্তি নয়, ভ্রান্তির প্রহসন, তা যেন তাদের জীবদ্দশাতেই তারা জেনে যায়। তাতে তাদের এই আশ্রয়ে সুদীর্ঘ অবস্থান হ্রস্ব হবে। প্রত্যেক মানুষেরই জীবনের যা শেষ এবং পরমগন্তব্য তাতে পৌঁছোতে কম সময় লাগবে।
এই নির্জনে সারাদিনই কথা বলি। কথা কাটি। কথা লিখি। কথা মুছে দিই লেখা হলে। ছায়াচ্ছন্ন নদীর গেরুয়া বালির ওপরে। কখনো কথা উড়িয়ে দিই পুলকভরে ঝরা-পাতার সঙ্গে। সারাটাদিন কথারই মধ্যে বাস করি কিন্তু শব্দ হয় না কোন। মুখ ফাঁক করতে হয় না।
প্রেমেন্দ্র মিত্র মশায় একবার একটি কথা বলেছিলেন আমাকে কলকাতাতে। আমি বলেছিলাম, যতটুকুই লেখালেখি করি, বড়ো কাটাকুটি হয়।
উনি তাতে হেসে বলেছিলেন, হোক না। কাটাকুটি হয় না কোন লেখকের? যা কিছুই বোঝাতে চেয়েছিলেন, বলতে চেয়েছিলেন তা একইবারে স্বচ্ছন্দে সাবলীলবাক্যে যিনি প্রকাশ করতে পারেন তিনি তো মহামানব!
তারপর হেসে বলেছিলেন, কেউ মনে কাটে আর কেউ লিখে কাটে। কাটে সকলেই। কাটাকুটির আর এক নামই তো সৃষ্টি।
তাই আমিও অনুক্ষণ কাটাকুটি করে যাই। এ অন্য কাটাকুটি। ইঁদুরদের কাটাকুটি নয়। ভাবনাহীন ভাবনা দিয়ে, অবলীলায় পাতা ভরিয়ে দিয়ে, সম্পাদকের হাতে পান্ডুলিপি তুলে দিয়ে তাঁর হাত থেকে চেক পাওয়ার পর নিজের ব্যাঙ্কের চেক কাটা নয় এ। এ কাটাকুটি অন্য কাটাকুটি। প্রেমেনবাবুর ভাষায় যে কাটাকুটির অন্য নাম সৃষ্টি।
লিখি, কাটি, ছিড়ি, আবার লিখি। ভারি আনন্দে আছি। সত্যিই বলছি।
বিনোদবিহারীবাবু ঠিকই লিখেছিলেন : নির্জনতা আমাদের কখনও শূন্য হাতে ফেরায় না।
তাই-ই হয়তো নির্জনে এলে, দেব-দেউলে এলে শূন্যহাতেই আসতে হয়।
.
০৮.
আজ পয়লা বৈশাখ। কলকাতায় থাকলে হয়তো বোঝা যেত। ইংল্যাণ্ডে থাকাকালীন দিশি নববর্ষকে তেমন করে উপভোগ করা যায়নি। এখানে প্রকৃতির দিকে চেয়ে গাছে গাছে। কিশলয়ের কচি-কলাপাতা সবুজের সমারোহে নববর্ষকে অন্তরের অন্তস্থলে অনুভব করছি।
হনসোর দাদার মেয়ের অসুখ হয়েছে শুনে গুটিগাড়ার দিকে যাচ্ছিলাম। পেটে অসহ্য ব্যথা। টোটকা-টাটকিতে সারছে না। কালই হাটে দেখা হয়েছিল হনসোর ভাইয়ের সঙ্গে। শুধু মিট্টি তেল কিনতে এসেছিল সে এতখানি পথ পেরিয়ে। বলছিল, মেয়েটি নাকি খুব অসুস্থ। মিশনের হাসপাতালে ভরতি করাবে দু-একদিনের মধ্যেই। চারঘণ্টা হাঁটাপথ ওদের গ্রাম গুটিংগাড়া। শালডুংরি থেকে।
সকালে নাস্তা করেই বেরিয়েছিলাম বুধবার দিন। গুটিংগাড়া যাব বলে। ওখানে হনুসোর ভাইঝির খবর নিয়ে একেবারে হাট করে ফিরে আসব এমনই ইচ্ছে ছিল।
মেয়েটির খোঁজ নিয়ে সন্ধের মধ্যেই ফিরে আসতে বলেছিল হনসো।
পথে একটি নদী পড়ে। নাম তার বড়োঝোড়া। ভারি সুন্দর সাদা প্রস্তরময় ভূমির ওপর দিয়ে বয়ে গেছে সর্পিল রেখায়। নদীটি যেখানে বাঁক নিয়েছে মহুয়াগড়-এর দিকে, সেখানে একটি হ্রদের মতো সৃষ্টি হয়েছে। সেই হ্রদের ঠিক পাশেই মাথা উঁচু মস্ত পাহাড়। তাতে বিরাট বিরাট গুহা। এইসব গুহাতে নাকি ভালুক থাকে অনেকই। হনসো বলেছিল একদিন। জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড় এবং গুহাগুলোদেখে মনে হল যে, থাকাই স্বাভাবিক। এই জায়গাটা লোকে একা তাই পার হতে চায় না সহজে দিনের বেলাতেও। দলে গেলেও টাঙ্গি বা বর্শা নিয়ে চলে। এই ভালুক বড়োই বদমেজাজি জানোয়ার। বেশিই বাঁশ আর ঝটিজঙ্গল এদিকে। মাঝে মাঝে দু-একটি শাল আছে। দলছাড়া।
নদীটা সবে পেরিয়েছি, পেরিয়ে একটা বাঁক ঘুরতেই দেখি একজন পাদরিসাহেব আসছেন। স্থানীয় কয়েকজন মুণ্ডার সঙ্গে। পাদরিসাহেবের চেহারা দেখে মনে হল বিদেশি তো বটেই তবে কন্টিনেন্টের লোক। ইংরেজ বা স্কট নয়।
বললাম, গুড মর্নিং।
বিদেশে থাকার এইসব বদভ্যাস ছাড়েনি এখনও আমাকে পুরোপুরি। আমরা ভারতীয়রাও গুড মর্নিং গুড ইভনিং বলি বটে, তবে চোখের ভাষাতে বলি, মুখে বলি না। চোখের ভঙ্গিতেই যা বোঝবার তা বোঝাই। মুখে বেশি কথা যারা বলে তারা বোঝায় না অত কিছু। দম-দেওয়া কলের মেশিনের মতোই বলে। কথারই কথা। অন্তরের সঙ্গে যোগ থাকে না সেইসব কথার। তা ছাড়া এক এক দেশের এক এক রকমের রীতি-নীতি; সহবত। ভারতীয়দের যে সাহেব হতেই হবে কেন তার কোনো মানে বুঝি না আমি। ইংরেজরা দুশো বছর দেশে শাসন করে এই শিক্ষাতেই আমাদের শিক্ষিত করে গেছে যে, যা-কিছু ইংরিজি তাই-ই ভালো। তাদের ভাষা, তাদের আদব-কায়দা, খানা-পিনা সব। এই নষ্ট করে দেওয়া ভারতীয়ত্বর মেরামতি কতদিনে সম্পূর্ণ হবে এবং কে কারা তা করবে আজ জানা নেই।
বিদেশি আমার চোখের ভাষা বুঝবেন না তাই-ই বলেছিলাম, গুড মর্নিং।
পাদরিও বললেন, গুড মর্নিং।
দাঁড়িয়ে কিছু কথা হল অল্পক্ষণ। হয়তো আমার ইংরিজি উচ্চারণ শুনে একটু অবাক হয়ে থাকবেন। আমার ইংরিজিটি হিন্দিরজি বা বাংলারজি নয়। এখনও নয়। তবে হয়তো হয়ে যাবে।
বললেন, আসবেন একদিন আমাদের চার্চ-এ। গল্প করা যাবে। এই ভালুগাড়ার চার্চ অনেকদিনের।
বললাম, আসব।
পাদরিসাহেব এবং তার সঙ্গীদের সঙ্গে দেখা হওয়ার পরই আর এক দল মানুষের সঙ্গে দেখা হল। ওদের কাছে ওই ফাদারের নাম জিজ্ঞেস করতে ওরা বলল, ফাদার ভিটার উইধাস। নাম শুনে মনে হল, জার্মান।
কেন জানি না, কিছু কিছু মানুষ থাকে যাঁদের দেখলেই মন ভালো লাগে। দেখেই মনে হয় যে, এঁরা ভালোমানুষ আর কিছু লোককে প্রথমবার দেখলেই বুকে ব্যথা করে, কথা বলতে ইচ্ছে করে না তাদের সঙ্গে, মনে হয় দিনটাই সপ্তাহটাই খারাপ যাবে। ফাদার উইধাসকে স্থানীয় লোকেরা ডাকে উধো ফাদার বলে। উধো ফাদারকে বেশ ভালো লেগে গেল।
আমাদের ডেরা থেকে এই গির্জাতে হেঁটে আসতে পঁয়তাল্লিশ মিনিট মতো লাগে। পরে একদিন এসে আলাপ করে যাব ওঁর সঙ্গে। এতদিনে ওঁর সঙ্গে দেখা যে কেন হয়নি জানি না। হাটে, মিশনের লোকজনকে দেখেছি। অন্য দু-একজন ফাদারকেও। তাঁদের চেহারা দেখে মনে হয়েছে গতজন্মে অনেক পাপ ছিল তাই-ই ক্ষালন করছেন এ জন্মে পাদরি বনে। ওই পাদরিদের মধ্যে একজনকে দেখে মনে হয় রীতিমতো কুচুটে, কুটিল; ঝগড়াটে।
হনসোর দাদার বাড়ি গিয়ে দেখি মেয়েটি আধঘণ্টা আগেই মারা গেছে। আজই সকালে ওরা হাসপাতালে নিয়ে আসত।
.
০৯.
হনসো মা হবে। আমি বাবা।
হনসো বলেছিল গ্রামের দাইমা-ই সবকিছু করবে। কিন্তু আমার পুরো ভরসা হয়নি। পুরোপুরি আদিবাসী হয়ে উঠতে পারিনি এখনও। এখনও আমার মধ্যে কিছু মেকি বাকি আছে। ভান আছে, অবিশ্বাস আছে। প্রশ্নাতীত বিশ্বাস ছাড়া পুরোপুরি কোনো কিছুই পাওয়া ভারি কঠিন। তা ছাড়া আদিম পৃথিবীর আদিম অধিবাসী হনসোরা। বাঙালি জাতের ইতিহাস তো ওদের মতো পুরোনো নয়। সত্যি সত্যিই ওদের মতো হয়ে উঠতে ভ্রষ্ট-হয়ে-যাওয়া আমার অনেকই সময় লাগবে।
অনেকদিন ধরেই ভাবছিলাম এবারে মিশনের ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বলার দরকার।
মিশনের একটি চমৎকার হাসপাতাল আছে। তবে ছোট্ট। মাত্র আটটি বেড। ফিমেল ওয়ার্ড-এ হাসপাতালটি ভালুগাড়ার চার্চ-এর কম্পাউণ্ডের মধ্যেই। হনসো যাই বলুক, ভাবলাম, ফাদার উইধাস-এর সঙ্গে ভালো করে আলাপও হবে। আর হনসোর ডেলিভারির ব্যাপারটা সম্বন্ধেও আলোচনা করে আসা যাবে। যদিও ওই হাসপাতালে মুখ্যত ক্রিশ্চানদের-ই চিকিৎসা হয় তবে আশা ছিল, আমি বললে ফাদার উইঘাস হয়তো রাজি হবেন।
ডেরা থেকে বেরোবার সময় ছলোছলো চোখে হনসো বলল, তুমি হাসপাতালে যাচ্ছ যাও কিন্তু আমি ওখানে ভরতি হব না। মরে গেলেও পরপুরুষকে আমি ন্যাংটো দেখাতে পারব না। এক তুমিই দেখেছ সবকিছু। তুমি-ই প্রথম। তুমিই শেষ। দাইমা-ই আমার যা করার করবে। তোমার ছেলে বলে বিশেষ কী? তার কি লেজ থাকবে?
এক একটি শব্দ প্রয়োগভেদে ব্যবহারভেদে কতই না বিভিন্নতা পায়। হনসো ন্যাংটা বা নাঙ্গা বোঝাতে অন্য কিছুকে বোঝাচ্ছিল আসলে।
আমার হাসি পেল।
বললাম, ঘুরে আসতে দোষ কী? ফাদারের সঙ্গে কথা বললেই তো আর…
ও বলল, ওখানে একজনও মেয়ে ডাক্তার নেই। আমি মরে গেলেও যাব না কিন্তু…
ঠিক আছে।
বলে, আমি বেরিয়ে পড়লাম।
ওদের উধো ফাদার যে এমন ইন্টারেস্টিং এবং পন্ডিত মানুষ তা সেদিন ভালুগাড়াতে না গেলে জানাই হত না। দীর্ঘদেহী, সৌম্যদর্শন, সাদা পোশাকের সেই ফাদার বসেছিলেন অফিসে। ওঁর অফিসের টেবিলের সামনে কিছুক্ষণ বসে থেকেই বোঝা গেল যে, অফিসে বসেও তাঁকে প্রচুর কাজ করতে হয়।
আমি যেতেই উঠে দাঁড়িয়ে, আমাকে উলটোদিকের চেয়ারে বসতে বলেছিলেন। ওই চেয়ারে বসেই লক্ষ করলাম যে, ফাদারের পেছনের দেওয়ালে একজন মোটাসোটা কালো জোব্বা পরা কাঁচা-পাকা দাড়িওয়ালা, চশমা-পরা একজন ফাদারের মস্ত ফোটো। নীচে, বড়ো বড় করে লেখা আছে, ফাদার জে. বি. হফম্যান, এস. জে.।
আমার চোখ এ দিকে পড়াতে ফাদার উইধাস বললেন, এই যে মানুষটির ফোটোটি দেখছেন এঁকে মুণ্ডারা তাদের ভগবান সিংহবাঙারই মতো মনে করে। ফাদার হফম্যানের যা অবদান তার তুলনা নেই।
আমি শুধোলাম, আপনি কি জার্মান, ফাদার?
ফাদার উইধাস বললেন, জার্মান যে, তা তো নাম শুনেই বুঝতে পারছেন। কিন্তু আমি সুইস-জার্মান। আপনি কি কখনো কন্টিনেন্টে গেছেন?
আমি মাথা হেলালাম।
তবে তো জানেনই যে সুইটজারল্যাণ্ডের পিঁও গিরিবর্ক্সর একপাশের মানুষ জার্মান-স্পিকিং আর অন্য পাশের মানুষ ফ্রেঞ্চ-স্লিকিং সুইটজারল্যাণ্ডের তত নিজস্ব ভাষা বলতে কিছু নেই।
হেসে বললাম, জানি।
কাজ শেষ করে উঠে ফাদার বললেন, চলো তোমাকে আমাদের হাসপাতাল, ডেয়ারি ফার্ম, পোলট্রি সব ঘুরিয়ে দেখাই!
বলেই বললেন, নট টু কনভার্ট। বাট টু ইমপ্রেস ইউ বাউট আওয়ার অ্যাকটিভিটিস।
বললাম, আমাকে কনভার্ট করতে পারবেন না ইচ্ছে করলেও। আমি যে খাঁটি ভারতীয়। আপনাদের অনেক কিছু ভালো জিনিস নিতে রাজিও ছিলাম যখন সাগর পারে ছিলাম, কিন্তু ধর্ম নেব কোন দুঃখে। হিন্দু বা বৌদ্ধ ধর্মর মধ্যে যারা একবার প্রবেশ করেছে, মানে সত্যিই গভীরে; আমি শুধুমাত্র রিচুয়ালস-এই বিশ্বাসী, মন্দিরের দেওয়ালে নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্যে মাথা-কোটা ধার্মিকদের কথা বলছি না; ধর্ম যাদের হৃদয়ের সত্যিই গভীরে পৌঁছেছে, যাদের ধারণ করেছে (ধর্ম মানেই তো ধারণ করা) তারা তোমাদের ধর্মর দিকে নিজের ধর্ম ছেড়ে খামোখা ঝুঁকতে যাবেই বা কেন? তা ছাড়া, সব ধর্মই তো এক।
ফাদার উইস আমার চোখে চোখ দুটি রেখে হেসে বললেন, তোমার বক্তব্য আরও প্রাঞ্জল করো।
আমি বললাম, আদিবাসীদের নিজেদের জীবনযাত্রা অক্ষুণ্ণ রেখেও তোমরা তাদের অনেক ভালো করতে পারতে। কিন্তু পশ্চিমি দুনিয়ার তোমাদের দোষই হচ্ছে এই যে, তোমরা যেটাকে ভালো বলে জানো, তার চেয়েও ভালো যে কিছুমাত্রই থাকতে পারে তা তোমরা আদৌ মানতে পারো না। মিনারাল-ওয়াটার, কমোড, বেসিন, টেবিল-চেয়ারে খাওয়া সেইসবকেও তোমরা ভারতীয় জীবনে অপরিহার্য করে তুলেছ কিন্তু…
ফাদার ইউধাস হাসছিলেন।
এবারে জোরে জোরে।
বললেন, মনে হচ্ছে, এই অঞ্চলে এতদিনে আমার সত্যিকারের একজন অ্যাডভার্সারি এল। তোমার সঙ্গে ঝগড়া করে আরাম হবে বলে মনে হচ্ছে। অনেক ঝগড়ার মুখ চেয়ে থাকব আজ থেকে।
আমিও হেসে বললাম, ঝগড়া না করলে, নিজেকে বিতর্ক আর প্রতিরোধের সামনে দাঁড় না করালে বার বার, মানুষ ঈশ্বরের যে গিফট-প্যাক-এ মোড়া অবস্থায় এই পৃথিবীতে আসে সেই মোড়ক না-খোলা অবস্থাতেই তো কফিনে ফিরে যেতে হয় তাকে। সে যে আদৌ মানুষ অথবা কোন ধরনের মানুষ তাই তো জানবার উপায় থাকে না কোন। তার নিজেরও।
ফাদার আবারও হাসলেন।
বললেন, আপনার সঙ্গে কথা বলে খুব আনন্দ পেলাম। আপনি কিন্তু ভুলে যাবেন না আমাকে। রোজ না পারেন একদিন অন্তর একদিন আসবেন। আমাদের দুজনের কাছেই দুজনের শেখার হয়তো অনেক কিছুই থাকতে পারে।
শেখাশেখির কথা কেন? আমি বললাম। খারাপ ছাত্র বলে কিছু শেখার কথা উঠলেই পালাতে ইচ্ছে করে।
উনি হাসলেন।
ফাদার উইধাস সব জায়গা-হাসপাতাল, ক্রেশ, লাইব্রেরি সব ঘুরিয়ে দেখালেন। যেকোনো গির্জার মধ্যে গেলেই ভারি ভালো লাগে আমার। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, ঝকঝক করছে সবকিছু। আমার মা বলতেন, পরিচ্ছন্নতার আর এক নাম হচ্ছে লক্ষ্মী। খ্রিস্টধর্ম সম্বন্ধে আমি বিশেষ কিছুই জানি না। কিন্তু হিন্দুদের বেশির ভাগ মন্দির এবং মন্দিরের পরিবেশ মোটেই তুলনীয় নয় কোনো গির্জার সঙ্গে, অন্তত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে। ধর্মস্থান, স্কুল, হাসপাতাল, বাজার, হাট এইসব দেখেই এক একটা জাতের চরিত্র, মানসিকতা এবং জীবনযাত্রার রকম সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করা যায়।
হনসোর কথা বলতেই বললেন একদিন নিয়ে আসবেন। আমাদের ডাক্তার আছেন ফাদার ডাফ। উনিও জার্মান দেখিয়ে গেলে ভালো হবে। এবং তারপরও রেগুলার চেক-আপ এর জন্যে আসতে হবে।
তারপর বললেন, আমাদের দিক দিয়ে কোনো অসুবিধেই নেই। অসুবিধে হয়তো আপনার স্ত্রীর-ইহবে। অনেক মেয়েরাই লেডি ডাক্তার না থাকাতে এখানে আসতে চান না। অনেক দিন থেকেই চেষ্টা চলছে। একজন লেডি ডাক্তার নান আসবেন পরের বছর। বেলজিয়াম থেকে! পরের বছর যদি তোমার আবার সন্তান হয় তখন কোনোই অসুবিধে হবে না।
আমি হাসলাম।
তারপর উনি মিশনের লাইব্রেরিতে নিয়ে গেলেন। লাইব্রেরিটি দেখে মুগ্ধ হয়েগেলাম। এই লাইব্রেরির লোভেই আমাকে বার বার আসতে হবে এখানে।
একটি বই তুলে দিলেন আমার হাতে ফাদার উইধাস। বললেন, আপনি মুণ্ডা মেয়ে বিয়ে করে স্বেচ্ছায় এই জংলি জীবন বেছে নিয়েছেন। কিন্তু মুণ্ডাদের জীবন-যাত্রা তাদের সামাজিক রীতি-নীতি, ধর্মীয় বিশ্বাস, ভাষা ইত্যাদি সম্বন্ধে যদি জানতে চান তবে এই বইটি পড়বেন। তাড়া নেই কোনো। আপনার সময়মতো পড়ে আমকে ফেরত দিয়ে যাবেন। একমাস রাখতে পারেন বইটি। যাঁর ফোটো দেখলেন আমার অফিসঘরে সেই ফাদার হফম্যান সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানতে পারবেন। ফাদার পি. পনেট, রাইট রেভারেণ্ড হ্যাঁন্স, ফাদার ডিনি ইত্যাদি অনেকের লেখা প্রবন্ধই এতে আছে।
ফাদার হফম্যান সম্বন্ধে জেনে আমার লাভ কী হবে? আমি বললাম। উনি বললেন, কোনো বই-ই কেউ সরাসরি লাভ-এর জন্যে পড়ে না। বই হচ্ছে সঁড়িপথ জঙ্গলের। কোন সঁড়িপথ যে কোন পথিককে কোন আলোতে পৌঁছে দেয় তা কি আগে থাকতে বলা যায়?
বা :! আমি বললাম।
তারপর ফাদার উইধাসকে ধন্যবাদ দিয়ে বইটি নিয়ে চলে এলাম।
.
১০.
কালকে কালবৈশাখীর মতো ঝড়-বৃষ্টি হয়ে গেলো। লক্ষ করছি প্রতিটি ঋতু পরিবর্তনের আগে বনে-জঙ্গলে ঝড়-বৃষ্টি হয়। ঝড়-বৃষ্টির পর নতুন ঋতু আসে। কাল বিকেল থেকেই শুরু হয়েছে ঝড়-বৃষ্টি। এখনও তার জের কমেনি। ঘর থেকে বেরোনোই যাচ্ছে না। তাই লণ্ঠনের আলোতে ফাদার উইধাসের দেওয়া বইটি নিয়ে বসলাম।
ফাদার হফফম্যান উনিশ-শো আটাশ খ্রিস্টাব্দে মারা যান। মারা যান অবশ্য জার্মানিতেই। জার্মানির সঙ্গে যখন ইংল্যাণ্ডের প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বাধে তখন শত্রুর দেশের লোক বলে তাঁকে ডিপোর্ট করা হয় এদেশ থেকে। কলকাতার বন্দরে যে জাহাজে চড়িয়ে তাঁকে ফেরত পাঠানো হচ্ছিল সেই জাহাজে এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটে যায়। তৎকালীন বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নর তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারিকে পাঠান জাহাজের ক্যাপ্টেনের কাছে। ক্যাপ্টেনকে বলা হয়, যে এই বন্দি সাধারণ মানুষ নন। তাঁর সঙ্গে যেন চমৎকার ব্যবহার করা হয় এবং যতদিন না জাহাজ জার্মানিতে পৌঁছোচ্ছে ততদিন ফাদার হফম্যানের যেন কোনোরকম অসুবিধে না হয় তা যেন অবশ্যই দেখা হয়।
সাঁইত্রিশ বছর আগে ভারতের ছোটোনাগপুরেই ছিলেন ফাদার হফম্যান। সাঁইত্রিশটি বছর একই জায়গায়। মাঝে মাত্র একবার দেশে গেছিলেন হৃত-স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্যে। আঠারোশো সাতাত্তরে কুড়ি বছরের এক নবীন যুবক ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাপোস্টোলিক ভিকারিয়েট-এ যোগ দেন। বেলজিয়ান ফাদারদের অধীনে ছিল তখন ওই অঞ্চলের পুরোটাই। বিহারের ছোটোনাগপুরের মালভূমিও তখন ওই পশ্চিমবঙ্গীয় ভিকারিয়েটের অধীনে ছিল।
পুরো সাঁইত্রিশ বছরই যে তিনি মিশনারি হিসেবে কাজ করেছিলেন তা অবশ্য নয়। সতেরো বছর শিক্ষানবিশ ছিলেন। আসেটিক এবং ইনটেলেকচুয়াল শিক্ষা পেয়েছিলেন। বাকি কুড়ি বছর অ্যাপোস্টেলেটের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। দুটি যুগ একজন মানুষের জীবনে এমনকিছু দীর্ঘ সময় নয়। কিন্তু মাত্র আটান্ন বছর বয়েসে তিনি যখন ভারতের মাটি ছেড়ে চলে যান তার আগেই যা কাজ তিনি একা হাতে করে গেছিলেন আদিবাসীদের জন্যে, তার কোনো তুলনা নেই। মুণ্ডাদের সভ্যতার ওপরে ওই সময়েরই মধ্যে উনি সম্পূর্ণ এনসাইক্লোপিডিয়া লিখে যান। অন্যান্য আদিবাসীদের জন্যেও ঋণ-পাওয়ার সুযোগ-সুবিধে, সমাবায় বিপণি ইত্যাদি অনেক কিছুই তিনি করে যান।
যদিও নিজের দেশে অনামা-অখ্যাত অবস্থাতেই মারা যান তিনি, কিন্তু এদেশের ব্রিটিশ অফিসার, মিশনারি এবং আদিবাসীদের কাছে তিনি যে সম্মানের আসনে বসেছিলেন তার কোনোই তুলনা নেই।
উনি জার্মান হলেও, ব্রিটিশ শাসকরা তাঁকে নিঃশর্তে বিশ্বাস করতেন। ছোটোনাগপুরের আদিবাসীদের জন্যে উনি যা করেছিলেন তার স্বীকৃতি হিসেবে উনিশশো তেরো খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার তাঁকে কাইজার-ই-হিন্দ খেতাবও দেন।
স্যার জাস্টিস টি এ সে ম্যাকফার্সন, সি আই ই, আই সি এস ওই মানপত্রে লিখেছিলেন, দেয়ার ইজ নো ডাউট দ্যাট হিজ লিঙ্গুইস্টিক স্টাডিজ অ্যাণ্ড সোসাল ওয়ার্ক হ্যাড রেণ্ডারড কাউন্টলেস সার্ভিসেস টু হিজ কলিগস ইন ছোটোনাগপুর। আই অ্যাম সার্টেন দ্যাট হিজ মনুমেন্টাল ওয়ার্ক অন দ্য মুণ্ডাজা উইল অ্যাট্রাক্ট দ্য অ্যাটেনশন অফ দ্য স্কলারস অফ দ্য হোল ওয়ার্ল্ড, হোয়ালস্ট ইন অ্যাগ্রারিয়ান ম্যাটারস হিজ কনট্ৰিব্যুশান টু আগ্রারিয়ান লেজিসলেশান রীচড ইটস ক্লাইম্যাক্স ইন দ্য ছোটনাগপুর টেনান্সী অ্যাযুক্ট মনুমেনন্টাম অ্যারে পেরেনিয়াম।