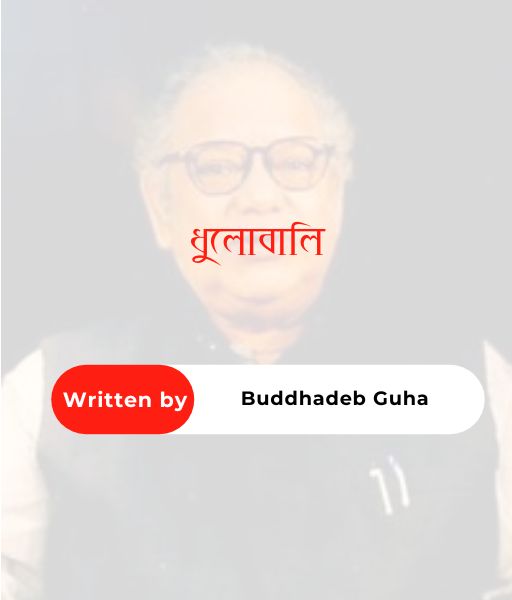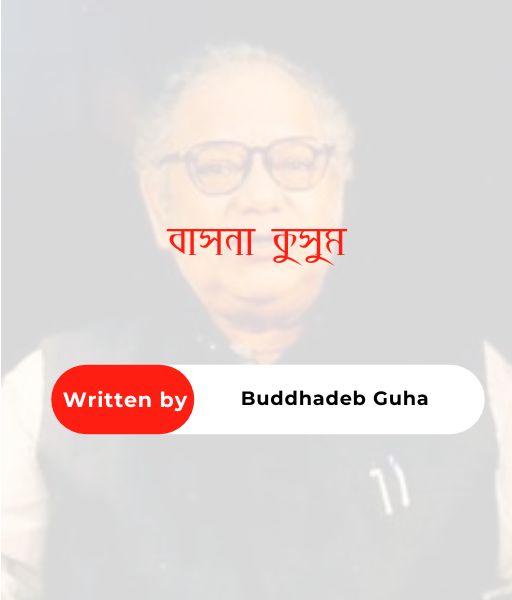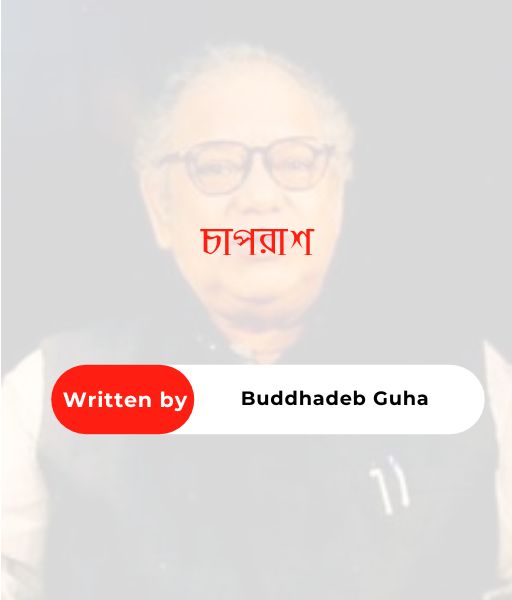রোণ্ডিয়া
০১.
রোণ্ডিয়া
পানাগড়
পশ্চিমবঙ্গ
স্যার জন অ্যাণ্ডারসন উনিশ তেত্রিশের দোসরা সেপ্টেম্বর রোণ্ডিয়া ব্যারাজ ওপেন করেন। দামোদরের ওপর। অনেক মেহগনি গাছ পুঁতে গেছিলেন সাহেবরা তখনই। রোণ্ডিয়া বাংলোটাও তখনই হয়।
বাংলোর হাতায় নানারকম গাছ আছে। নতুন নতুন অনেক ফুলের গাছও লাগিয়েছেন, নতুন একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, শ্ৰী আর এন দে। কাঠ-কাঞ্চন,কাঞ্চন, টগর, কামিনী, নানা ফুল। গেটের ডান পাশে দুটো মেহগনি দেখলাম। মেহগনির পাতাগুলোতেও যেন সোনার ঝিলিক। শিরীষও আছে। নিম, দেবদারু, কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া, চাঁপা, আম, কাঁঠাল, করবী, সোনাঝুরি, গন্ধরাজ, জুই, বেল, বোগেনভিলিয়া, কেয়া, জবা, সজনে।
ব্যারাজের ডান দিকে দামোদরের বুকে একটি হ্রদের মতো সৃষ্টি হয়েছে। বর্ষার মেঘমেদুর বিকেলে বাঁ-দিকের সোনালি বালির বিস্তীর্ণ চরকে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে। চরের পাশে পাশে মাঝে মাঝে কাশ ও শরের চিকন-সবুজ শরীর, পড়ন্ত বিকেলের বিধুর আলোর মতো সোনালি বালির চরের পটভূমিতে, ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে। জেলেরা ব্যারাজের বাঁ-দিকে যেদিকে জল পড়ছে, সেখানে বাঁধ-জাল পেতে চিতল, কালোবাউস আর বাটামাছ ধরছে।
দ্বিজপদ আঁকুড়া চৌকিদার।
জেলেদের মধ্যে নানান জাত আছে। রাজবংশী, আঁকুড়া ও জেলে। এখন আর পেশাভেদে জাতভেদ নেই। পেটের জন্যে যে-যা করে। বাঁধের বাঁ-পাশে ফতেপুর কসবা গ্রাম। নদীর ওপারে আছে মানা গ্রাম। মানা ক্যাম্প থেকে উদবাস্তুরা বহুদিন আগে এসে ওখানে বাসা বেঁধেছিল। সন্ধের আগে আগে মেয়েরা মাথায় হাঁড়ি-কলসি নিয়ে বাটামাছ কিনে চরের ওপর দিয়ে কাশিয়া আর শরের মধ্যে মধ্যে হেঁটে যাচ্ছে মানার দিকে।
এ মানা, অন্য মানা।
রোণ্ডিয়ার আগের গ্রাম চাকতেঁতুলের বাউরি পাড়াতে দু-বছর আগে একরকম পোকার উপদ্রব হয়েছিল, মশার মতো। সেই পোকার কামড়ে বহুলোক মারা যায়। ওরা জাতে বাউড়ি। চাকতেঁতুল গ্রাম এখনও ঠিকই আছে। শুধু বাউড়িপাড়া থেকে ওরা এসে এখন ব্যারাজের নালার পাশে খড়ের অথবা কাঠের ঘর করে রয়েছে। ওরা নাকি গ্রামের মনসা ও কালীমাকে অসম্মান করেছিল।
শেষ-বিকেলে উদলা গায়ে চান সেরে, বিকেলের আলোতে টানটান ভিজে স্তনে মসৃণতা ছড়াচ্ছে লাল-শাড়িপড়া বাউড়ি মেয়ে। নীলকণ্ঠ পাখি উড়ে যাচ্ছে ভাবরির ঘনায়মান ঝোঁপের ওপর দিয়ে সবুজ জমির আস্তরণ পেরিয়ে। একটা কালো ঘাড়ে-গর্দানে রোমশ কুকুর একটি দুর্বল বাদামি কুকুরিকে কামোন্মেত্ত হয়ে তাড়া করেছে। কুকুরিটা ল্যাজ দিয়ে স্ত্রী-অঙ্গ ঢেকে একেবারে জলের কোনায় চলে গিয়ে শ্লীলতা রক্ষার জন্য জলের দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তবু মরদের হুশ নেই।
বক উড়ছে বাঁধ-জালের ওপরে ওপরে-বাঁধ থেকে জোর জল পড়ার শব্দ আসছে মস্তিষ্কের মধ্যে দূরের স্মৃতির সোনাঝুরি শব্দের মতো। দামোদরের পাড়ে গ্রামে গ্রামে সন্ধে হওয়ার শব্দ উঠছে আলতো হয়ে। পশ্চিমের সন্ধেতারার সবুজ দ্যুতির দীপ্তি পাচ্ছে।
কসবা-মানার পাশে চম্পাইনগরে মাঘ মাসে মস্ত মেলা বসে-বেহুলা-লখিন্দরের স্মৃতিতে। তার পাশে সাঁতালি পর্বতে (ন্যাড়া, উঁচু ঢিপি) লখিন্দরের বাসরঘর ছিল নাকি! মেলাতে চুড়ি, পেতলের থালাবাসন, ছাতা, জুতো, কাঠের জিনিস, দরজা-জানলা, পাথরের বাসন এইসব ওঠে। শাড়ি, ধুতি, গামছা, ম্যাজিক, পুতুল-নাচ, সার্কাস, নাগরদোলা।
চাকতেঁতুলে চৈত্র মাসে গাজনের মেলা বসে। বিশ তিরিশ ফুট ওপর থেকে বঁটির ওপরে ঝাঁপ দেয় গাজনের সন্ন্যাসীরা।
রোণ্ডিয়াতে ও কসবাতে (কেউ কেউ কাহেবাও বলে) এবং চাকতেঁতুলেও শিবমন্দির আছে।
হাটটা আগে রোণ্ডিয়াতেই বসত। হাটের মাশুল নিয়ে মন কষাকষি হওয়াতে হাট এখন রোণ্ডিয়া থেকে ফোতোপুরের পথে যেতে যে-মোড় আছে, যেখানে আটাকল, তার পাশে বসে। একটা পুকুর। তাতে সবজে-নীল জল। পুকুরপাড়ে নিমগাছের সারি। পাড়ার দু-পাশে নিমগাছ। নিমফল এসেছে আষাঢ়ের শেষে। আঁশফল, তাল, বাবলা, বেল এবং কৃষ্ণচূড়াও আছে। তরি-তরকারি, শাড়ি, গামছা, লুঙ্গি, প্লাস্টিকের জুতো-চটি, চুড়ি, নানারকম কাঁচের গয়না, টিপ, ইঁদুর-মারা ওষুধ, মাছ-ধরার পোলো, পাকৌড়ি-ফুলুরির দোকান, মাছ, মুরগি, হাঁস, চাল, নিরোধ সব সুন্দর পাশাপাশি।
রোদে-পোড়া চিকন কালো টানটান চেহারার মানুষজন। আঁটো-করে পরা গোড়ালির অনেক উঁচুতে তোলা শাড়িতে কিশোরী। ব্লাউজের ফাঁকে ফলসা রঙা আঁটসাঁট স্তন। তার ঘামের গন্ধ, কামের গন্ধ, ধুলোর গন্ধ, জলের গন্ধ, চিটেগুড়ের গন্ধ, সব মিলেমিশে গেছে।
পরেশনাথ গুপ্তর দেশ উত্তরপ্রদেশের গাজিপুরে। এখানে এসে সে দামোদরের পাড়ে খড়ের ঘর বানিয়ে চা-এর দোকান দিয়েছে। সঙ্গে মাছের কারবারও করে। বাটা, চিতল, কালবাউশ, চিংড়ি, ট্যাংরা, সোনা-ট্যাংরা, আড় কত মাছ। আর কদিন বাদে ইলিশও উঠবে। কী যে স্বাদ ইলিশের। বেশি উঠলে, টাকায় দু-তিনটেও পাওয়া যায়।
পরেশের কালো ভুটিয়া-কুকুরি লক্ষ্মী, শুয়ে শুয়ে দোকানের সামনে দামোদরের হাওয়ায় ঘুমোয়। আজ একটা জুই আড় উঠেছে। শ-য়ে একটা ওঠে। মুখ-ছোটো আড়।
বাঁধের ওপর কালো পাথরের ডাঁই। এদিকে ওদিকে ফণিমনসার ঝোঁপ। অশ্বত্থ, সেগুনের চারা গজিয়ে উঠেছে। সেখানে বড়ো বড়ো সাপ থাকে। গোখরা, চন্দ্ৰবোড়া, শঙ্খচূড়। মাছ খায়। কখনো কামড়ায় না কাউকে।
লখিন্দরকেই কামড়ে ছিল শুধু।
নীলমণি আগে পানাগড়ের মিলিটারি ক্যাম্পে রাজমিস্ত্রির কাজ করত। ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছে। বুক-খোলা নীল হাফশার্ট আর লুঙ্গি পরনে। মাছের ব্যাবসা করে। আসলে সেটা একটা ছুতো। রোজগার কমই হয় তাতে। কিন্তু ও স্বভাবে কবি। দামোদরের পাশে হু-হুঁ হাওয়ায় বসে, লাল ঘোলা জল আর চাপ চাপ নরম স্বপ্নিল সবুজ ঢালে, দূরের খড়ে-ছাওয়া ঘরের দিকে চেয়ে নীলশাড়ি পরে ঘুরে-বেড়ানো গোবর-লেপা উঠোনে সজনে গাছের তলায় তার প্রেমিকা সোনামণি ঘুরে ঘুরে মুরগির জন্যে ধান ছিটোয়। ও দেখে, ভালো লাগে। যাত্রার গান বাঁধে মনে মনে। দুটি বইও লিখে ফেলেছে নীলমণি। পালার বই। সি পি এম করে ও। পালাতে, সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশা, আসা-আকাঙ্ক্ষার কথা লিখেছে ও।
ক্লাস নাইন অবধি পড়েছিল।
হাটে আলাপ হল সোবেদ মন্ডলের সঙ্গে। পোলো বিক্রি করছিল। কী সুন্দর হাতের কাজ। বাঁশ আর সুতো দিয়ে কী সুন্দর করে বানিয়েছে। বাঁশি বাজায় ও অবসর সময়ে। ওর বাজনার দল আছে। বাঁশি, ক্ল্যারিয়োনেট, ড্রাম। মাঝে মাঝে লোকাল ট্রেনে চেপে কলকাতায় জানবাজারে গিয়ে যন্ত্র কিনে নিয়ে আসে। বিয়ে-চুড়োতে বায়না পায়, মাঝে মাঝে বাজনা বাজাবার। আনন্দ ছাড়াও দুটো পয়সাও আসে ঘরে।
এখানের পঞ্চায়েত ইলেকশন প্রায় সবই, সি পি এম জিতেছে। নির্দল, জনাচার। ইন্দিরা কংগ্রেস এক। বি ডি ওর জিপ আসে গুটুর-গুটুর আওয়াজ তুলে। মেহগনি গাছের ছায়ায় ছায়ায় লাল মোরামের রাস্তা বেয়ে বাঁধের ওপরের পথ বেয়ে বর্ধমানের দিকে চলে যায়।
ইরিগেশন ডিপার্টের অ্যাসিসট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার দত্তসাহেব বলেন, আমি এখান থেকে কেটে পড়বই। দেখবেন। এমন বাজে জায়গায় কেউ থাকে?
তা ছাড়া, লোকগুলো মহা ঝামেলার। ওই তো খুন হল, সেদিন বাঁধের ওপর। সন্ধেরাতেই।
রোণ্ডিয়ার বাগানে বুলবুলি, টুনটুনি, মৌটুসকি, পাখিরা ভিড় করে। গভীর রাতে নদীর পাড়ে পাড়ে টিটি পাখি ডেকে ফেরে। চাতক পাখিরা দলবেঁধে ফটিক-জল ফটিক-জল বলে উড়তে থাকে চাঁপাগাছের মাথায়, সন্ধের আগে আগে। বাঁধের পাশের সবুজ চালের গায়ে ভাবরির জঙ্গলে নীল কাঁচপোকা ওড়ে, ছাগল চরে, পরম আত্মতৃপ্ত মুখ নিয়ে। মৌমাছি ওড়ে, গুনগুন করে।
নদী থেকে আসা হাওয়াটা হঠাৎ থেমে যায়। মেঘ করেছে। গুমোট। জল হবে একটু পরে।
এই রোণ্ডিয়া উয়্যার এবং এই পরেশ গুপ্ত, নীলমণি, এদের নিয়ে একটি গল্প লিখব কখনো। নীলমণিকে নায়ক করে। গল্পে ওর নাম দেব, সনাতন আঁকুড়া। আর গল্পের নাম : লতুল পালা। যে-পালা লিখছে এখন নীলমণি।
চরে হেঁটে বেড়াচ্ছিলাম। বৃষ্টিভেজা ঘুঘুর বিষণ্ণ ডাক যেন বুকের মধ্যে ছুরি চালিয়ে দেয়। নিজের বুকের বেদনাতুর হৃদয়কে স্থানে স্থানে কে যেন, তীক্ষ্ণ কোনো অস্ত্র দিয়ে অমোঘ নিরুত্তাপ হাতে, ধীরে-সুস্থে, ঠাণ্ডা-মাথায় জবাই করে। শেষবিকেলের মরা আলো উথালপাথাল হাওয়ায় ঝিলিক মারে ভাবরি আর ভেরেণ্ডার বনে। লাল ভেরেণ্ডার গাছগুলো ভারি সুন্দর। পাতাবাহারের মতো লাল-কালো চিকন উজ্জ্বল পাতা। টুনটুনি পাখি ডাল দুলিয়ে উড়ে যায় কাশিয়ার ঝোপেভরা চরের দিকে। পাখির নীচু হয়ে উড়ে যাওয়ার গতির সঙ্গে গতিম্মান হয় আমার চোখ। যেখানে নদী মিশেছে দিগন্তে, বালির চর, কাশিয়া আর শরবন মিশেছে নদীতে, আর আকাশ মিশেছে মেঘে। মন সেখানে পৌঁছে, চোখের দিগন্তকে বিদ্ধ এবং অতিক্রম করে কল্পনার এবং স্মৃতির পশ্চিমাকাশে ধ্রুবতারা হয়ে ফুটে উঠতে চায়।
এ-জীবনে চাওয়ার দুঃখ, না-পাওয়ার দুঃখ এবং পাওয়ার দুঃখও এই বর্ষাবিধুর নদীর চরেরহু হু হাওয়ায় আমার সমস্ত ভিজেমনকে উথালপাথাল করে।
.
০২.
কলকাতা
আজ সন্ধেবেলায় রবীন্দ্রসদনে সুরসাগর হিমাংশু দত্তের লেখা ও সুরারোপিত গান শুনতে গেছিলাম। আমাদের বাবা-মায়েদের যৌবনযুগের পরিচিত সব প্রিয়গান।
রবীন্দ্রসদনে সাবিত্রী ঘোষ এসেছিলেন। তিনিই প্রথম গাইলেন।
গান এখন তেমন ভালো লাগল না। দু-বার জল মুছলেন চোখের। এত বছরের দূরত্বেও ভালোবাসা চোখের জল দাবি করতে পারে?
বিশ্বাস হয় না, এই অবিশ্বাসের যুগে।
হয়তো সে-যুগের মানুষেরা অনেক সৎ ও আন্তরিক ছিলেন। আমি যদি কাউকে সুরসাগরের চামেলির মতো ভালোবেসেও থাকি, তাহলেও তার চোখে আমার মৃত্যুর সাতদিন পরেও হয়তো জল থাকবে না। সে-যুগের চামেলিরা আজকাল ফোটে না। জমি খারাপ হয়ে গেছে। কলুষিত হয়ে গেছে। হয়তো সেই চাঁদও আর ওঠে না। পরিমন্ডলে এত ধোঁয়া-ধুলো বিষ যে, চাঁদের আলো আর তেমন করে চামেলির কাছে পৌঁছোয় না।
আমাদের বাঙালি প্রেম ওঁদের লায়লা-মজনুর প্রেমের মতো খ্যাতি লাভ করেছে। হিমাংশু দত্ত নিশ্চয়ই আমার চেয়েও বেশি রোমান্টিক ছিলেন। এবং স্বভাবতই মূর্খ। সাবিত্রী ঘোষকে আজকে দেখার পর সত্যিই কষ্ট হল। সুরসাগর তো কবেই চলে গেছেন। এই ধরনের অশরীরী রোমান্টিক ভালোবাসা একমাত্র ভারতীয়রাই সে-যুগে বাসতে পারতেন। আজকে বোধ হয়, ঠিক ওইরকম ভালোবাসা আর কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। কোনো দেশেই।
তবে সেই যুগে তিনি, যথেষ্ট সাহস দেখিয়েছেন। গানের মধ্যে দিয়ে নিজের প্রেমিকাকে পরিচিত জগতে একটা চিরস্থায়ী আসন করে দেওয়ায় এবং সেই প্রেমের ভূমিকাকে চাঁদ ও চামেলির মাধ্যমে নিজেদের দুজনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে যাওয়ার মূল্য কী এবং কতটুকু তা প্রেমিক-প্রেমিকামাত্রই জানেন। সুরসাগরের প্রেম, গান এবং সমস্ত আত্মবঞ্চনা বিফল হয়নি। কারণ, এখনও চামেলির চোখ দিয়ে তীব্র আলো-জ্বালা মঞ্চে বসে-থাকা অবস্থাতেও চাঁদের জন্যে জল পড়ে। সেই চাঁদের জন্যে, যে-চাঁদ চিরদিনই মেঘের পারেই ছিল; পৃথিবীর চামেলির কাছে যার কখনোই নেমে আসা হয়নি।
আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ভারতীয় গণ্ডার এবং সিংহের মতো এমন প্রেমিক-প্রেমিকাও আজ বড়োই বিরল হয়ে উঠেছেন।
প্রেম ব্যাপারটি দেহাতীত, সময়াতীত; বয়সতীত এবং কালাতীতও। তবুও অশরীরী প্রেমে একসময়ে বিশ্বাস করলেও আজ আর করি না। অমন প্রেমের একটা বয়েস থাকে শরীর এবং মনের। তারপর নিজের মানসিকতার পটভূমি বিস্তৃততর হতে থাকলে, অভিজ্ঞতার মেঘে পরত লাগতে থাকলে তখন অন্যরকম মনে হয়। যাকে ভালোবাসি, তার শরীরে যেতে, শরীরকে পেতে; বড়োই ইচ্ছে করে। আবার এও ঠিক, বড়ো দুঃখজনকভাবে ঠিক যে, পাওয়ার পরমুহূর্তেই তার শরীরের উষ্ণকোরকে নিজের শরীরের প্রাণ নিংড়ে দেওয়ার মুহূর্তেই, চমকের সঙ্গে আবিষ্কার করতে হয় যে, শরীরটা কিছুই নয়। শরীরে কিছুই নেই, মনটাই সব।
আবারও তবু কিছুদিন পরই প্রেমিকার শরীরের প্রতি তীব্র আকর্ষণ জাগে। আমাকে যে তার অদেয় কিছুই নেই, তাকে শরীরের সমস্ত অণুপরমাণু দিয়ে ভরিয়ে নিয়ে এবং তার শরীরকে ভরে দিয়ে, নিজেকে, নিজের আত্মবিশ্বাস এবং আত্মশ্লাঘাকে বার বার পুনরুজ্জীবিত করতে ইচ্ছে যায়।
আসলে শরীর আর মন এমনভাবে জড়িয়ে আছে যে, একটা থেকে অন্যটাকে আলাদা করা যায় না। মনের ভালোবাসার বৈচিত্র্য, গভীরতা ও আনন্দ অনেক বেশি তীব্র, কিন্তু শরীরও ভালোবাসা চায়। তাকে উপবাসে রাখলে মনের ভালোবাসার স্ফুরণ হয় না। শরীর না পাওয়ার আগে যে তীব্র ভালোবাসা, যাকে কামগন্ধহীন প্রেম বলে জানা আছে। আমার মতে, তার মতো তীব্র কামগন্ধি প্রেম আর হয় না।
সত্যিকারের প্রেমের উন্মেষ ঘটে, শরীরে খিদে পুরোপুরি মিটিয়ে নেওয়ার পরই।
সুরসাগরের গানের মধ্যে আরতি দত্তর (আগেকার মালা দাস?) গান বড়ো ভালো লাগল। কত বয়েস হয়েছে। কিন্তু কী চমৎকার গলা! তখনকার দিনের গায়ক-গায়িকাদের মধ্যে ফাঁকি ছিল না। প্রত্যেকেরই রাগপ্রধান গানের ভিত ছিল, যে-কারণে গলায় তানবিস্তার অতিসহজে আসত।
কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়, উমা বোসের গাওয়া দুটি গান গাইলেন। কিন্তু উমা বোসের গলা ভগবানদত্ত ছিল। কৃষ্ণা খুব ভালোই গেয়েছেন কিন্তু মনে হল, প্রাণপণে উমা বোসের কাছাকাছি আসতে চাইছেন। অনুকরণে কেউ কি কখনো কোনো আদিকে ছাপিয়ে যেতে পারেন? উমা বোস হওয়ার মতো চেষ্টা না করে, নকল না করে, নিজের গায়কিতে গাইলেই ভালো করতেন উনি। ওঁর গলা তো বেশ ভালোই। কিন্তু এমন এমন কিছু গায়ক-গায়িকা থাকেন তাঁদের গলা অনুকরণ করা যায় না। তাঁরা তাঁরাই। তাঁরা ঈশ্বরপ্রেরিত।
এইসব গলা ভগবানের দান। চেষ্টা করে, কসরত করে একটা জায়গা পর্যন্ত পৌঁছোনো যায়–জীবনের সবক্ষেত্রেই, কিন্তু শিল্প ও কলার ক্ষেত্রে সাধারণের একটা সীমারেখা থাকে। যাঁরা সেই সীমার ওপারে পৌঁছোন, তাঁরা ঈশ্বরের আশীর্বাদসম্পৃক্ত। তাঁদের অনুকরণ করতে গেলে, অনুকরণকারীর সামান্যতাই বড়ো নগ্নভাবে প্রকট হয়ে পড়ে।
দ্বিতীয়ার্ধে অখিলবন্ধু ঘোষের গান ভালো লাগল। সুরসাগরের গান। কিন্তু প্রত্যেকটি গান শচীনকর্তার গাওয়া। তাঁর প্রথম দিকের গান। অখিলদার কিন্তু দাঁত-বাঁধিয়ে নেওয়া উচিত অবিলম্বে। নইলে, এত ভালো গান সব ফসফস করে হাওয়া হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।
তা ছাড়া, লাল প্লাস্টিকের গ্লাসে কী যেন, খাচ্ছিলেন। ওঁর হাবভাব, অঙ্গভঙ্গি দেখে মনে হল মদ। অনেক শিল্পীর এমন হয়ে থাকে, মদ না খেলে, গাইবার সময় আত্মবিশ্বাস থাকে না। এও এক ধরনের ব্যাধি! এবং আত্মবিশ্বাসের ঘাটতির প্রমাণ। মদই কি খাচ্ছিলেন?
মাঝেমধ্যে মদ আমিও খাই। গান গাইবার সময় খেলে, গান গাইতে ভালোও লাগে এবং মনে হয় গলা খুলে যায়। আরও গান গাইতে ইচ্ছে করে। ফলে একটা বিপজ্জনক সময় আসে যখন শ্রোতারা শুনতে না-চাইলেও আমার মতো অ-গায়কের উৎসাহ তাঁদের প্রায় ধরেবেঁধে গান শোনাতে বাধ্য করে।
যাঁরাই অত্যাচারিত হয়েছেন, তাঁরাই জানেন।
বাইরের অনুষ্ঠানে শিল্পীদের আর একটু সংযমী হওয়া প্রয়োজন। তাতে শিল্প এবং শিল্পীদুইয়েরই সম্মান বাড়ে।
একথা শিল্পীদের চেয়ে বেশি প্রযোজ্য, এযুগের বিজ্ঞাপনের ডঙ্কানিনাদিত, উচ্চমন্য, কবি সাহিত্যিকদের প্রতিও।
অখিলদার সামনে হয়তো চা অথবা অন্য কোনো পানীয়ও ছিল। আন্দাজে কোনো মন্তব্য করাটা ভদ্রজনোচিত কাজ নয়, আমি ভুলও হতে পারি।
গানের একটা মস্ত সুবিধে এই-ই যে, গায়কের বিচার হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু সাহিত্য কাব্যের বিচার হয় ধীরে ধীরে। অতি ধীরে ধীরে। পাঠক-পাঠিকার মস্তিষ্কের কোষে কোষে, সেই রস নিঃশব্দে চুঁইয়ে যায়। তাই সাহিত্যিক কে, সাহিত্যিক হয়েছেন কি হননি; তা জানতেই অনেক বছর অপেক্ষা করতে হয়, তাঁর সাহিত্যকর্ম প্রকাশিত হওয়ার পরও।
যে-গায়ক মঞ্চে বসে বা রেকর্ডে খারাপ গান করেন তাঁকে শ্রোতারা বাতিল করেন তৎক্ষণাৎ। কিন্তু কবি-সাহিত্যিককে বাতিল করেন পাঠকেরা অনেকই পরে।
গায়কের মৃত্যু, সরল, তাৎক্ষণিক, কিন্তু সাহিত্যিকের মৃত্যু বিলম্বিত। তাই-ই অত্যন্ত বেদনাদায়ক।
.
০৩.
কলকাতা
আমার বিশেষ পরিচিত এক তরুণ দম্পতির প্রথম সন্তান পরমা সুন্দরী ছ-মাসের মেয়ে সকেটি হঠাৎ-ই মারা গেল।
শোক, আমাদের অনেক কিছু বুঝিয়ে ও জানিয়ে দিয়ে যায়, যা-আমরা প্রবহমান জীবনস্রোতে ভেসে ভুলে থাকি।
ওদের এই চিঠিটা লিখেছি। পড়ে, কালই আমাকে ফেরত দিয়ো।
মিনু ও রাহুল,
বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতোই শুনলাম যে, তোমাদের চোখের মণি ছোট্ট সকেটি হঠাৎ ই চলে গেছে।
তোমাদের শোকে সান্ত্বনা দেব এমন মনোবল, পান্ডিত্য ও গভীরতা আমার নেই। আজ গিয়েও তোমাদের কাছে মুখে কিছুই না বলতে পেরে ফিরে এলাম। তা ছাড়া একাও পাইনি তোমাদের।
প্রত্যেকের জীবনেই এমন অনেক মুহূত আসে যখন বুকে অনেক কথা থাকলেও; তা মুখে বলা যায় না। কিছু বলতে পারিনি। তাই-ই এই চিঠি।
আমি শুধু এইটুকুই বলব যে, তোমাদের শোক যদি তোমাদের একারই বলে মনে করো, তাহলে তোমরা তোমাদের নিজেদের এবং অন্যদের প্রতিও অবিচার করবে। তোমাদের দুঃখে ও হতাশায় তোমরা দুজন একা নয়। সকলেই তোমাদের দুঃখ সমানভাবে ভাগ করে নিয়েছে। ভাগ নিয়েছে তোমাদের দুঃখের, এমন একজনের জন্যে, যেকথা বলতে জানত না, যে তোমাদের মা-বাবা বলে এখনও ডাকতে পর্যন্ত শেখেনি। নাম পর্যন্ত স্থিরীকৃত হওয়ার আগেই যে সকলকে কাঁদিয়ে চলে গেছে। যার যাওয়ার বড়োই তাড়া ছিল।
কিন্তু সত্যিই কি তোমাদের আদরের প্রথম শিশুসন্তান, যাকে তোমরা অনেকই স্বপ্ন আর কল্পনা দিয়ে তিল তিল করে গড়েছিলে, তোমাদের ছেড়ে চলে গেছে?
আমি জানি, তোমাদের বর্তমান মানসিক অবস্থায়, তোমাদের এ-প্রশ্ন করা বোধ হয় ধৃষ্টতা। তোমরা এও মনে করতে পারো যে, তোমাদের শোকের ভাগীদার আমি নই। মনে করতে পারো যে, তোমাদের কাছে আমি অতিমানব সাজবার চেষ্টা করছি। তোমরা গীতা পড়েছ কি না জানি না। না পড়ে থাকলে, পোছড়া। শান্তি পাবে। আসলে সকেটি তোমার আমার মতো পাপী-তাপী কেউ নয়। আমাদের মতো পূর্বজন্মের পাপ তার জমা ছিল না। ফুলের মতো মেয়ে, ফুলের পোশাক পরে তার ছ-মাসেরছোট্টজীবনের মেয়াদ শেষ করে পরমমুক্তি লাভ করেছে। যারা রইলাম, আমরা সকলে, তোমরাদুজন; হয়তো পূর্বজন্মে অনেক পাপ করেছিলাম ও করেছিলে, তাই-ই এই ফুল-হারানোর শোকের ব্যথা আমাদের প্রত্যেকের পাওয়ার ছিল।
কিন্তু সে তোমাদেরেও ছিল কি? তোমাদেরই যে ছিল, সে-সম্বন্ধে তোমরা এমন নিঃসন্দেহ কেন? কী করে? সে যাঁর দান, যাঁর অঙ্গুলি হেলনে সে তোমাদের কাছে এসেছিল, তাঁরই নির্দেশে সে,তাঁরই কাছে ফিরে গেছে। এই দুয়ারটুকু পার হতে তোমাদের এবং আমাদের অনেক সংশয় ছিল এবং আছে। কিন্তু শিশু নিঃসংশয়ে সেই দুয়ার পেরিয়ে চলে গেছে। দু-দিক দিয়ে ঘেরা ঘরে তার বেশিদিন থাকতে ভালো লাগেনি; তাই-ই চলে গেছে। চিরদিনের ঘরে।
গীতাতে নান্যং ছিন্থন্তি পাবকঃ ইত্যাদি সংস্কৃত শ্লোক আছে। আমি রাধাকৃষ্ণাণের ইংরেজি ভাষ্যে গীতা পড়েছি। সংস্কৃত জানি না বলে। উনি লিখেছেন :
The Bhagabatgita speaks of the spirt of man as immortal.
Weapons do not cleave the self, fire does not burn Him, water do not make Him wet, not does the wind make Him dry.
He is uncleavable, He cannot be burnt, He can be neither wet nor a dried, He is immortal, eternal, all pervading, unchanging, immoveable, He is the same forever.
অন্য এক জায়গায় বক্তৃতা দিতে গিয়ে রাধাকৃষ্ণাণ বলেছিলেন :
Man is more than the sum of his appearances.
When Crito asked Socrates : In what way shall we bury you, Socrates?
Socrates answered : In any way you like, but first catch me; the real me. Be of Good cheer, my dear Crito, and say that you are burying my body only, and do with whatever is usual and what you think best.
তোমরা কি তার শরীরকেই এত ভালোবেসেছিলে? সমস্ত তাকে কি ভালোবাসোনি? যদি না বেসে থাকো, তাহলে সে এখন তোমাদের দিকে চেয়ে যেমন মিষ্টিহাসি হাসত, তেমনই হাসছে। যে-ডাক ডাকার মতো সময় হাতে নিয়ে সে আসেনি, সেই ডাকেই বলছে : মা। বাবা! তোমরা কী বোকা! আমার পোশাকটাকেই ভালোবেসেছ, আমার সত্যি আমিকে একটুও ভালোবাসোনি তোমরা। তোমরা খুবই খারাপ!
আমি শুনলাম যে, ওকে তোমরা কবরে শুইয়ে রেখেছ। ভালোই করেছ। কিন্তু যারা সকলকেই কবরে শোয়ায় শরীরের জীবন শেষ হলে, তারা কোন মন্ত্র পড়ে শোয়ায়, তা জানলে হয়তো তোমাদের মন একটু শান্ত হত।
হিন্দুধর্মে বলে যে, আত্মা অবিনশ্বর; আত্মার বিনাশ নেই। খ্রিস্টানরা তা বলেন না। কিন্তু শরীরকে কবরস্থ করার সময়, তাঁরা যে-মন্ত্র পড়েন তার সঙ্গে হিন্দু দর্শনের এতই মিল দেখি যে, মনে করতেই হয়, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই কোনো-না-কোনোভাবে মেনে নিয়েছেন যে, আত্মা অবিনশ্বর।
খ্রিস্টানরা কাউকে কবরস্থ করার সময় বলেন :
Thou knowest, Lord, the secret, of our hearts, shut not thy merciful ears to our prayer, but spare us, Lord most holy, Oh God most mighty, Oh holy and merciful saviour, thou most worthy Judge eternal suffer us not, at our last hour, for any pains of death to fall from thee.
We, therfore commit his body to the ground, Earth to Earth, Ashes to Ashes, dust to dust in sure and eternal hope of resurrection to eternal life.
যে-রবীন্দ্রনাথ আমার তোমার মতো সাধারণ মানুষ নন, তাঁর জীবনে বাইশ বছর বয়েসের প্রথম শোকের কী অনুভূতি, তা পড়লে হয়তো তোমাদের মন একটু শান্ত হবে। উনি লিখেছিলেন–
জীবনের মধ্যে কোথাও যে কিছুমাত্র ফাঁক আছে তাহা তখন জানিতাম না; সমস্তই হাসিকান্নায় একেবারে নিরেট করিয়া বোনা। তাহাকে অতিক্রম করিয়া আর কিছুই দেখা যাইত না, তাই তাহাকে একেবারে চরম করিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলাম।
এমন সময় কোথা হইতে মৃত্যু আসিয়া এই অত্যন্ত প্রত্যক্ষ জীবনটার একটা প্রান্ত যখন একমুহূর্তের জন্যে ফাঁকি করিয়া দিল, তখন মনটার মধ্যে সে কী ধাঁধাই লাগাইয়া দিল। চারদিকে গাছপালা মাটিজল চন্দ্রসূর্য গ্রহতারা তেমনি নিশ্চিত সত্যেরই মতো বিরাজ করিতেছে অথচ তাহাদেরই মাঝখানে তাহাদেরই মতো যাহা নিশ্চিত সত্য ছিল, এমনকী দেহ প্রাণ হৃদয় মনে সহস্রবিধ স্পর্শের দ্বারা যাহাকে তাহাদের সকলের চেয়েই বেশি সত্য করিয়াই অনুভব করিতাম সেই নিকটের মানুষ যখন এত সহজে একনিমেষে স্বপ্নের মতো মিলাইয়া গেল তখন সমস্ত জগতের দিকে চাহিয়া মনে হইতে লাগল এ কী অদ্ভুত আত্মখন্ডন। যাহা আছে এবং যাহা রহিল না এই উভয়ের মধ্যে কোনোমতে মিল করিব কেমন করিয়া।
জীবনের এই রন্ধটির ভিতর দিয়া যে এক অতলস্পর্শ অন্ধকার প্রকাশিত হইয়া পড়িল, তাহাই আমাকে দিনরাত্রি আকর্ষণ করিতে লাগিল। আমি ঘুরিয়া ফিরিয়া কেবল সেইখানে আসিয়া দাঁড়াই, সেই অন্ধকারের দিকেই তাকাই এবং খুঁজিতে থাকি–যাহা গেল তাহার পরিবর্তে কী আছে!
শূন্যতাকে মানুষ কোনমতেই অন্তরের সঙ্গে বিশ্বাস করিতে পারে না। যাহা নাই তাহাই মিথ্যা, যাহা মিথ্যা তাহা নাই। সেই অন্ধকারকে অতিক্রম করিবার পথ অন্ধকারের মধ্যে যখন দেখা যায় না তখন তাহার মতো দুঃখ আর কী আছে।
তবু এই দুঃসহ দুঃখের ভিতর দিয়া আমার মনের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে একটা আকস্মিক আনন্দের হাওয়া বহিতে লাগিল তাহাতে আমি নিজেই আশ্চর্য হইলাম। জীবন যে একেবারে অবিচলিত নিশ্চিত নহে, এই দুঃখের সংবাদেই মনের ভার লঘু হইয়া গেল। আমরা যে নিশ্চল সত্যের পাথরে-গাঁথা দেওয়ালের মধ্যে চিরদিনের কয়েদী নহি, এই চিন্তায় আমি ভিতরে ভিতরে উল্লাস বোধ করিতে লাগিলাম।
যাহাকে ধরিয়াছিলাম তাহাকে ছাড়িতেই হইল, এইটাকে ক্ষতির দিক দিয়া দেখিয়া যেমন বেদনা পাইলাম তেমনি সেইক্ষণেই ইহাকে মুক্তির দিক দিয়া দেখিয়া একটা উদার শান্তি বোধ করিলাম।
বাড়ির ছাদে একলা গভীর অন্ধকারে মৃত্যুরাজের কোনো একটা চূড়ার উপরকার একটা ধ্বজপতাকা, তাহার কালো পাথরের তোরণদ্বারের উপরে আঁকপাড়া কোনো একটা অক্ষর কিংবা একটা চিহ্ন দেখিবার জন্য আমি যেন সমস্ত রাত্রিটার উপর অন্ধের মতো দুই হাত বুলাইয়া ফিরিতাম।
আবার সকাল বেলায় যখন আমার সেই বাহিরের পাতা বিছানার উপরে ভোরের আলো আসিয়া পড়িত তখন চোখ মেলিয়াই দেখিতাম আমার মনের চারিদিকের আবরণ যেন স্বচ্ছ হইয়া আসিয়াছে। কুয়াশা কাটিয়া গেলে পৃথিবীর নদী গিরি অরণ্য যেমন ঝলমল করিয়া ওঠে জীবনলোকের প্রসারিত ছবিখানি আমার চোখে তেমনই শিশিরসিক্ত নবীন ও সুন্দর করিয়া দেখা দিয়াছে।
তোমরা দুজনেই শিক্ষিত, বুদ্ধিমান ও বুদ্ধিমতী। মিনুর মতো বুদ্ধিমতী মেয়ে খুম কমই হয়। কিন্তু আমি জানি যে, জগতের সব বুদ্ধি জড়ো করেও এমন সব মুহূর্তের শোক লাঘব করা যায় না। শোক লাঘব করাটাও ভালোকথা নয়। জীবনে, সমস্ত কিছুরই এক বিশেষ ভূমিকা আছে। জীবনে মৃত্যুর যে-ভূমিকা, তার চেয়ে বড়ো ভূমিকা বোধ হয় আর কিছুরই নেই। শোকের মতো বড়ো শিক্ষা ও শুদ্ধি বোধ হয় হয় না।
কিন্তু আমরা সকলেই জানি যে, যা মৃত তাই-ই অমৃত। কারণ মৃত্যুর হাত ধরেই আমরা পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হই। যস্য ছায়া মৃতম তস্য অমৃতম। আসলে আমরা যারা নিঃশ্বাস ফেলছি বা প্রশ্বাস নিচ্ছি তারাও সর্বক্ষণ মৃত্যুর ছায়াতেই বেঁচে আছি। হিন্দুধর্মে বা বৌদ্ধধর্মে আত্মার মরণ নেই। আত্মা শুধু পোশাক বদল করে। করতে করতে একসময় পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হয়ে যায়। এ-মুহূর্তে এটা বিশ্বাসের কথা। তর্কের কথা নয়। যুক্তির কথা নয়। তোমাদের বর্তমান মানসিক অবস্থাতে যদি এ-কথাটার তাৎপর্য মনে-প্রাণে বিশ্বাস করার চেষ্টা করো তাহলে শান্তি পাবে।
অন্যদের ধর্মগ্রন্থও, যেমন বাইবেল ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একই কথা বলছে। বাইবেলে একটা অধ্যায় আছে The order for the burial and the dead তার থেকে সামান্য উদ্ধৃতি দিচ্ছি, পড়ে দেখো তোমরা দুজনে।
We brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out. The Lord gave and the Lord hath taken away; blessed be the name of the Lord.
সব ধর্ম, সব শাস্ত্রই বলছে যে, He never continues in one stay. তাই-ই আমাদের বিশ্বাস করতে হয়ই যে, শরীর বদলাতে পারি হয়তো আমরা, কিন্তু প্রাণের মৃত্যু নেই।
Josehp Hall লিখেছিলেন
Death did not first strike Adam, the first sinful man, nor Cain, the first hyporoite, but Abel, the innocent and righteous– the first soul that met death overcame death, the first soul parted from earth, went into Heaven—- Death argues not displeasure, because he whom God loved best dies first, and the murderer is punished with living.
আরও অনেক কথা বলতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু রাত দুটো বেজে গেছে। তা ছাড়া তোমাদের মনকে শান্ত করি এমন সাধ্য আমার কোথায়? শান্ত করলে, তা তোমরা নিজেরাই তা করতে পারবে। বাইরের কেউই পারবে না। দুজনে একা থাকো, খুব কাছের লোক ছাড়া দূরের লোকদের ভিড়ে থেকো না। বই পড়ো, নিজেরাই নিজেদের শোককে বহনযোগ্য করে তুলতে পারবে। শোক ভোলা মানে, সকেটিকে ভোলা নয়।
সে তো আনন্দের মধ্যে দিয়েই এসেছিল, আনন্দ দিতে এসেছিল, আনন্দের মধ্যেই চলে গেছে, আবারও ফিরে আসবে বলেই। হয়তো অন্য নামে, অন্য শরীরে। সকেটি আছে, থাকবে। তোমরা ওকে সত্যিকারের আপন বলে মনে করোনি, ওকে ওর নিজের মহিমার আসনে বসাওনি বলেই, ওর এই লুকোচুরি খেলাতে তোমাদের সমস্ত গড়ে তোলা স্বপ্নই মনে হচ্ছে গুঁড়িয়ে গেছে। সে আছে, স্বর্গে আছে।
যা গুঁড়িয়ে গেছে তা আমার আমার বোধ।
আমি যা প্রথমেই বলেছি, তাই আবারও বলছি, সে যে তোমাদেরই দুজনের একারই ছিল,এ-সম্বন্ধে তোমরা এত নিঃসন্দেহ হলে কী করে? সংসারে আমার বা তোমার কীই বা নিজের? কিছুই যে নিজের নয়, সেই কথাই বুঝিয়ে দেন ভগবান আঘাত দিয়ে।
রাহুল ও মিনু, তোমাদের কাছে আমার মিনতি, তোমরা তোমাদের শোককে সকলের সঙ্গে সমান করে ভাগ করে নাও। ভাগ করে নিয়ে, নিজেদের হালকা করো, ওদের প্রত্যেককে হালকা করো। তোমরা যদি কান্নাকাটি করো, দুঃখে থাকো, তবে সকেটির ফিরে আসতে দেরি হবে টালমাটাল পায়ে তোমাদের কোলের কাছে। তাকে ডাকো। তাড়াতাড়ি কোলে তুলে নাও। নতুন করে গড়ো, পুরোনোকেই মিনু, তোমার শরীরে; রাহুল, তোমার দানে।
চিঠিটা কালই পাঠিয়ে দিয়ো কিন্তু। অত্যন্ত অভিভূত অবস্থায় লিখেছি বলেই চিঠিটা লিখে অস্বস্তি বোধ করছি। আমি তো তোমাদের মতো আঁতেল নই যে, সব ভাবাবেগকে গলা টিপে মেরে ফেলাকে শিক্ষার সমার্থক বলে মনে করি!
.
০৪.
সিনক্লেয়ার হোটেল
শিলিগুড়ি
সেই জানুয়ারি মাসে শান্তি আর জেসমিনকে নিয়ে পালামৌর মারুমারে গেছিলাম। তারপর আর বেরোনোই হয়নি। যেভাবে দিনেরাতে আঠেরো ঘণ্টা কাজ নিয়ে মাস কাটে আমার, তাতেমাঝে-মাঝেই কলকাতার বাইরে চলে না যেতে পারলে বাঁচাই মুশকিল।
কলকাতার বাইরে যাওয়ার কথা উঠলেই ম্যাকলাস্কিগঞ্জের কথা মনে পড়ে। একটু উষ্ণতার জন্যে উপন্যাসে ম্যাকলাস্কিগঞ্জ ধরা থাকবে চিরদিনের মতো।
আমার ধারণা যে, কোয়েলের কাছের মতোই এই উপন্যাসও ধীরে ধীরে জনপ্রিয় হয়ে উঠবে এবং যতদিন যাবে, ততই কদর বাড়বে এর।
রবীন্দ্রনাথ বলতেন, যা হৃদয়ের যত গভীর থেকে ওঠে, তা অন্য হৃদয়ের তত গভীরে গিয়ে পৌঁছোয়। আমি সে-কথায় বিশ্বাস করি। সাহিত্যে ভঙ্গি, মেকি-ইন্টেলেক্টের বানানো বাণ, চমক ইত্যাদির চেয়ে শ্লথগতি অথচ সুখপাঠ্য আপাত-সাধারণ অথচ অত্যন্ত গভীর অনুভূতির অভিব্যক্তিচিরদিনই বেঁচে থাকে পাঠক-পাঠিকার হৃদয়ে।
যুগে-যুগে পাঠক বদলায়, তার মানসিকতা বদলায়, পোশাক-আশাক, খাদ্য-পানীয়, জীবনযাত্রার ধরন এবং অনেকানেক বোধও বদলায়। তবুও মনে হয়, মানুষের মনুষ্যত্বব্যঞ্জক বহুবিধ বোধ ও অনুভূতি চিরদিন একই থাকে, যেখানে মানুষ এক, শাশ্বত এবং গোঁড়া। গোঁড়া কথাটা আপেক্ষিক। গোঁড়া শব্দটির সঙ্গে মূলের কোনো গভীর আত্মিক সাযুজ্য আছে। মানুষের মনের এক বিশেষ এলাকায় গুহামানব আর চাঁদে পা দেওয়া মানুষে তফাত বিশেষ দেখি না। বিবর্তনের ঢেউ সেই গভীরে প্রোথিত মূল অনুভূতির শিকড়কে ধুয়ে নিতে পারেনি এতদিনেও। ভবিষ্যতেও যে পারবে, তা মনে হয় না।
যাইহোক, ম্যাকলাস্কির কথা বলতে গিয়ে অন্য কথায় চলে এলাম। ম্যাকলাস্কির দ্য টপিং হাউস বিক্রি করে দেওয়ার আগে ওই জঙ্গলের গভীরের কটেজটিকে যে কতখানি ভালোবাসি, তা একটুও বুঝতে পারিনি। রীণা কিনতে চাইল। ঋতু সমেত সকলকেই বলেছি যে, রীণার সুন্দর মুখের অনুরোধ ফেলতে পারলাম না। কোনো সুন্দর মুখই জীবনে আমার কাছে কিছুমাত্র চেয়ে কখনো না উত্তর পায়নি। রীণাকেও না করতে পারিনি। তখন টাকার প্রয়োজনও ছিল। যাকে বলে, গট ইট ফর আ সং তাই-ই পেল, ও। যদিও, গান না গেয়েই।
আর্নেস্ট হেমিংওয়ের আইডাহোর বাড়ির নাম ছিল দ্য টপিং হাউস। জঙ্গল পাহাড়ের মধ্যে। হেমিংওয়ের বাড়ির নামে নাম রেখেছিলাম আমার কটেজের। হেমিংওয়ে ওই নামের বাড়িতেই আত্মহত্যাকরেছিলেন। শোয়ার সময় মাথার বালিশের নীচে লোডেড পিস্তল রাখার দরুন, এক রাতের দুর্ঘটনায় আমিও এক রাতে মরতে বসেছিলাম ম্যাকলাস্কির দ্য টপিং হাউসে।
মিথ্যে বলব না, মাঝে মাঝেই মরতে তো ইচ্ছে করেই। ডিপ্রেশানের এক একটি সাইকেল আসে ঘুরে ফিরে, বারে বারে। কখন যে তার নীচে তলিয়ে গিয়ে কী করে বসব তা যে আমি নিজেও জানি না!
বড়ো বড়ো নিমগাছগুলো, ঝুপড়ি আমগাছ, শাল আর পলাশের জঙ্গল–যে-জঙ্গলের একটিও গাছ কাটতে বারণ করেছিলাম আমি। ছোটোকাকু একবার বেড়াতে গিয়ে জঙ্গল হয়ে গেছে দেখে কিছু গাছ কেটেছিলেন বলে আমি ক্ষুব্ধ হয়ে ওঁকে বলেছিলাম, জঙ্গল করেই রাখতে চাই এই জঙ্গলের বাড়ি। কারিপাতা গাছ, ফলসা গাছ, চেরিগাছ, প্লাম গাছ, পিচ গাছ, কত ফুল, কত পাখি আর কী নিবিড় গভীর প্রশান্তি। আমার লেখার ঘরটি–লেখার ঘরের জানলা দিয়ে চোখমেলা আদিগন্ত সবুজ, ঘন সবুজ পাহাড়। বর্ষার দিনে পাহাড়-চুড়ো থেকে গড়িয়ে আসা এক্সপ্রেস ট্রেনের মতো শব্দ-ওড়ানো বৃষ্টি। বৃষ্টির গন্ধ, বৃষ্টির পরে বন পাহাড়ের গায়ের গন্ধ; কোনো ভালোবাসার জনের চান করে ওঠার অব্যবহিত পরের গায়ের গন্ধেরই মতন।
বসন্তের দিনের মহুয়া আর করৌঞ্জের গন্ধ, ওঁরা ওদের মাদল-বাজানো গান, পিউ-কাঁহা আর কোকিলের সারারাতব্যাপী চাঁদের আলোয় মোহময় বনের বুক থেকে চমকে চমকে ডেকে ওঠা শীতের রাতে, টালির ছাদে বাড়ির আশপাশে শিশির পড়ার ফিসফিস শব্দ। ফেব্রুয়ারিতে শিয়ালদের নালার গভীরে চিৎকৃত মিলনের রব। গ্রীষ্মের ভোরে হাজার পাখির ডাকে সূর্যোদয়ের আগে ঘুম ভাঙা। বুলবুলি, টুনটুনি, কতরকম মৌ-টুসকি, টিয়ার ঝাঁক, ক্রো ফেজেন্ট, ব্যবলার, থ্রাশার, মিনিভেট, ওরিওল। কতরকমের রং-বেরঙের ফ্লাই-ক্যাচার। পাখির জগৎ।
ও-বাড়িতে আর যেতে পারব না। রীণা বলেছিল, বছরে দু-বার আমি যখন খুশি যেতে পারি, যতদিন খুশি থাকতে পারি।
কিন্তু মানি, মুঞ্জরি আর ওই বাড়ির সঙ্গে, সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়েছি চিরদিনের মতন। মানুষ কিংবা সম্পত্তি আমি সম্পূর্ণ মালিকানা ব্যতীত কখনোই ভোগ করতে পারিনি। আমার মন মানে না। যা- আমার পুরোপুরি নয়, তা সম্পত্তিই হোক কী মানুষই তোক তার ওপর কোনো অধিকার বর্তাতে পারিনি আমি কোনোদিনই। যাকে আমি পুরোপুরিই আমার বলেই জানি, আমার যেকোনো দাবি, যেকোনো আবদার, যেকোনো অত্যাচারই মানতে রাজি; সেই-ই আমার।
ওই বাড়ি, জীবনের হারিয়ে-যাওয়া একাধিক নারীরই মতো, আর আমার নেই।
বুকের মধ্যে মাঝে মাঝে বড়ো মুচড়ে-মুচড়ে ওঠে। বিরহই মানুষকে বুঝতে শেখায়, মিলনের গভীর আনন্দ। প্রিয়জনের সঙ্গে আশ্লেষে, ঘোরে, যখন অঙ্গাঙ্গি হয়ে থাকা যায়, তখন মিলন খরস্রোতা নদীর মতোই বয়ে যায়। সেই নদীর আবর্তের মধ্যে থাকাকালীন নদীর চেহারাটা একেবারেই প্রতীয়মান হয় না। জলের স্রোতের গতি, পায়ের নীচের বালি, গায়ের পিছলে-যাওয়া রোদ এইসবে মিলন মাখামাখি হয়ে থাকে। সেই মিলনের নদীর সৌন্দর্য তখনই পুরোপুরি পরিস্ফুট হয়, যখন দূরের বিরহের পাহাড়-চুড়ো থেকে সেই মিলনের নদীকে দেখতে পাওয়া যায়।
আমার মনে হয় প্রাপ্তির মধ্যে, সম্পত্তির মধ্যে, মিলনের মধ্যে সত্যিকারের সুখ নেই। প্রাথমিক সুখ, প্রাপ্তির আশায়, কামনায়, মিলনের কল্পনায়। আর শেষ এবং সার্বিক সুখ একসময় প্রাপ্ত সম্পত্তি এবং মিলনের স্মৃতিতেই। মিলনকালে ভালোবাসার যে-গভীরতা থাকে, বিরহে তার ব্যাপ্তি ঘটে। দূরে না গেলে, দূর থেকে না দেখলে; কিছুই যথার্থ মূল্য পায় না।
মাঝে মাঝে নিজেকেও নিজের মধ্যে থেকে বাইরে বের করে নিয়ে দূরে চলে যেতে হয়। তখন সমস্ত জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে, পাওয়া-না-পাওয়া, সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, বিরহ মিলন সবকিছুই ভাস্বর হয়ে স্বচ্ছ ও দেবদুর্লভ প্রকৃত সত্যমন্ডিত হয়ে ওঠে। তাই, যা হারিয়ে যায় তাই-ই পরম ধন হয়ে থাকে। আর যা, আমারই মালিকানায় থাকে, তার দাম বুঝি না। কাছে থাকে বলেই বুঝি সে, চোখজুড়ে থাকে। তাকে ভালো করে দেখতে পর্যন্ত পাই না। দূরে গেলেই তার সৌন্দর্য, তার নরম হৃদয়ের দ্যুতি সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে।
যা বলতে বসে শিলিগুড়ি থেকে চিঠি লেখা, তাই বলা হল না! এবারে কমিশনারদের সঙ্গী হিসেবে জলপাইগুড়ি এলাম। উঠলাম ভান্ডাগুড়ি চা-বাগানের অতিথিশালায়। শিকারপুরের পাশে। এই শিকারপুর জলপাইগুড়ির রাইকত রানি প্রতিভা দেবীর। যখন তিনি আমাদের মক্কেল ছিলেন তখন, এই বাগানে একাধিকবার এসেছি। সরস্বতীপুর বাগানেও গেছিলাম ওঁরই সঙ্গে। শিকারপুরের কাছেই ভান্ডাপুর বাগান ছিল। সন্ন্যাসীকাটা হাট। আনন্দমঠের। সরস্বতীপুরের সীমানায় দাঁড়িয়ে তিস্তার যে- রূপ দেখেছিলাম তা ভোলার নয়। উলটোদিকে আপাল চাঁদের জঙ্গল, কাঠামবাড়ির ফরেস্ট বাংলো। আর ওপাশে চ্যাংমারির চর।
জলপাইগুড়ির রানি প্রতিভা দেবীর স্বামী ছিলেন ড. কিরণ বোস। জ্যোতি বসুর আপন দাদা।ড. বোস গত হয়েছেন। আমি ডাকতাম কিরণকাকু বলে।
সকালে উঠে ব্রেকফাস্ট করে জলপাইগুড়ি গেলাম। জলপাইগুড়ি ক্লাবে অফিসারেরা কমিশনারদের লাঞ্চ খাওয়ালেন। লাঞ্চ-টাঞ্চ খেয়ে আমরা গোরুমারা স্যাংচুয়ারির দিকে রওনা হলাম, শ্রী ও শ্রীমতী টি ওয়াই সি রাও এবং শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সেনের সঙ্গে। শরদিন্দু ভট্টাচায্যি মশায়ও ছিলেন আমাদের সঙ্গে।
মাল হয়ে বিকেল বিকেল গিয়ে পৌঁছোলাম। পাশেই একটি চা-বাগান। পুলিশ-ফাঁড়ি দিয়ে স্যাংচুয়ারিতে ঢুকতে হয়। যে-জায়গায় গোরুমারা বাংলোটি, সেটি সমতলে। বাংলোর হাতার সীমানায় একটি কাঠের বারান্দা মতো–বাইরে বের করা। নীচে সোজা নেমে গেছে খাড়া পাড়, প্রায় পাঁচ-শ ফিট। খাড়া পাড়ের পা ধুয়ে বয়ে চলেছে একটি নদী, তার নাম ইনডং। দূরে পাথর-ছড়ানো একটি সুন্দর নদী চোখে পড়ে, এঁকে বেঁকে চলে গেছে। তার নাম মূর্তী। জানোয়ার দেখে মানুষ, সেই বারান্দায় বসে। বারান্দার সোজা সামনে, গাছ কেটে গ্লেড মতো করা হয়েছে। প্রায় আধমাইল অবধি তিনদিকে চোখ যায়। নীচেই সল্টলিক তৈরি করা হয়েছে। মেকি। দু-পাশে দুটি প্রকান্ড শিমুল গাছ। একটি শুকনো সাদা ডালের শিমুল। তার চুড়োয় বসে সোনালি বাজ ডানা ঝাড়ছে। ল্যাজ ঝুলিয়ে অস্তগামী সূর্যের দিকে মুখ করে বসে আছে প্রকান্ড ময়ূর।
দুটি শুয়োর এল।
চারদিক থেকে ময়ুর ডাকছে আর হনুমান।
সন্ধের পর চাঁদ উঠল না। অন্ধকার রাতে তারারা একে একে আকাশময় ফুটে উঠল। বাংলোর নীচে ঘাসের ওপর চেয়ার পেতে বসে আমরা গল্প করছিলাম। দূরের হিমালয়ের বুকে আলেয়ার মতো আলো জ্বলে উঠছিল মাঝে মাঝে, পরক্ষণেই নিভে যাচ্ছিল।
ভট্টাচায্যি সাহেব বললেন, এ-আলোগুলো চলার পথের গাড়ির হেডলাইট। আশ্চর্য লাগে দেখলে। মনে হয় আকাশপথে কোনো অশরীরী আত্মা আলোকবর্তিকা নিয়ে যাওয়া-আসা করছে।
শিলিগুড়ি ফিরে, বিকাশ পাঙ্খাবাড়ি রোড ধরে মকাইবাড়ি, কার্শিয়াং-এ নিয়ে গেল। পাঙ্খাবাড়ির পথের মতো খাড়া পথ, এ-অঞ্চলে কমই আছে। যতটুকু পথ সমতলে, সেখানে হাতির বড়োই উপদ্রব। মকাইবাড়ি বাগানের মালিক পশুপতি ব্যানার্জি এবং মালিকপুত্র রাজার সঙ্গে আলাপ হল। অ্যালসেশিয়ান ও হরেকরকম কুকুরে বাড়ি ভরতি। মকাইবাড়ির চাও খাওয়া হল।
কার্শিয়াং-এ মাসিমার বাড়িতেও গেলাম ডাউহিলে। বড়োই মন খারাপ হয়ে গেল বাড়ি দেখে। ওঁর চাতুরীতেও মন কম খারাপ হল না। চাতুরী আমাকে বড়ো ব্যথিত করে। আমার সঙ্গে যাঁরা চাতুরী করেন, তাঁরা প্রায়ই হারেন। একজন বড়ো বিচারক প্রায়ই চতুরদের হারিয়ে দেন, অদৃশ্য আদালতের অমোঘ রায়ে।
মহানদী ফরেস্ট বাংলোতে রিজার্ভেশন ছিল। পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে গেলামও। কিন্তু সেখানে না আছে খাওয়ার জল, না আছে স্নানের জল। তা ছাড়া এক-দাঁতি গণেশ-মহারাজ নাকি বাংলোর মধ্যে ঢুকে, প্রায় রোজই অত্যাচার করছেন। সেভক রোডের উলটোদিকের বস্তিতে লোক মেরেছেন, ঘর ভেঙেছেন।
এ-বাংলোতেও গোরুমারারই মতো জানোয়ার দেখার বন্দোবস্ত। নীচে আর্টিফিশিয়াল সল্টলিক। তিস্তা এদিকে অনেকটা সরে এসেছে। অনেক জঙ্গল ধুয়ে নিয়ে গেছে। জলস্রোত বইছে কাছেই।এদিকের বাঁধ ভেঙে গেলে তিস্তায় শিলিগুড়ি শহরকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে কোনোদিন। বড়ো সর্বনাশা নদ-এ। পুরুষ হাতির মস্তির সময় সঙ্গিনী না পেলে সে যেমন, অসীম কামমত্ত ও সর্বনেশে হয়ে ওঠে, প্রতিবর্ষায় তিস্তারও সেই অবস্থা।
এই দুর্দান্ত নদকে শিগগিরই কোনো শান্ত স্নিগ্ধ নদীর সঙ্গে বিয়ে দেওয়া দরকার।
কালকে গয়াবাড়ি-ফুকুরি-সোনাইরী হয়ে মিরিক গেছিলাম। মিরিক কমলালেবুর জন্য বিখ্যাত। একটা আর্টিফিশিয়াল লেকও খুঁড়েছে এখানে। পাশে ট্যুরিস্ট বাংলোও হচ্ছে নতুন।
সৌন্দর্যর বাবদে খোদার ওপর খোদকারি আমার দু-চোখের বিষ। সারাভারতের ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে স্বাভাবিক বুদ্ধিসম্পন্ন ও সৌন্দর্যজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ বোধ হয় খুব, কমই আছেন। নইলে, স্বাধীনতার পর পর বিভিন্ন রাজ্যের জঙ্গলে যেখানে যেখানেই এইসব ব্যক্তিদের হাত পড়েছে, সেখানে সেখানেই প্রকৃতির স্বাভাবিক ও অনাবিল সৌন্দর্যকে কদর্য করা হয়েছে। কবে যে এঁদের সুবুদ্ধি এবং সুরুচি হবে জানি না।
গোরুমারা স্যাংচুয়ারির বাংলোতে কুক নেই। মহানদীতেও নেই। অসম-বিহার-ওড়িশার বাংলোর চৌকিদাররা কত যত্ন করেই না, রান্না-টান্না করে দেয়। পশ্চিমবঙ্গের মতো এমন ঢিলে, যত্নহীন, দায়িত্বজ্ঞানহীন বনবিভাগ খুম কম আছে। যদিও দুর্নীতিতে ওড়িশা এবং বিহার এগিয়ে। কলকাতার এত কাছে এমন এমন ভালো সমস্ত জায়গার বাংলোগুলো সম্বন্ধে বনবিভাগের বৈমাত্রেয় মনোভাব দেখলে চোখে জল আসে। সরকার এবং সরকারি আমলারা জনসাধারণের সেবক নন এই গণতন্ত্রে। তাঁরাই হলেন জনসাধারণের মালিক। তাদের ভয় দেখানো জুজু। আদর না দিয়েই এঁরা শাসন করতে চান।
মিরিকের রাস্তার তুলনা হয় না। পাহাড়জোড়া চা-বাগানগুলোকে মনে হয় যেন সবুজ গালিচা। কাঞ্চনজঙ্ঘার ওপরে শেযসূর্যের আলো পড়ে কী অপূর্ব যে দেখাচ্ছিল, তা কী বলব। ফুকুরী চা-বাগানের কাছটাও ভারি সুন্দর। মিরিক, কার্শিয়াং এবং দার্জিলিং-এর চেয়ে অনেক নির্জন, অনেক সুন্দর।
এখানে কোনো পাহাড়ের ওপরে একটু জমি পেলে বাড়ি করতাম।
নির্জনে লেখাপড়া করার এমন জায়গা হয় না।
.
০৫.
কলকাতা
আজ আত্মসমালোচনার দিন। নিজেকে নিয়ে, শোয়ার ঘরের দরজা বন্ধ করে, অন্য মনে আয়নার সামনে বসে স্বগতোক্তির স্রোতে ভেসে-যাওয়ার দিন। জীবনের ভারে একেবারেই চাপা পড়ে গেলাম। স্রোতের শ্যাওলার মতো ভেসে চলেছি আঘাটার দিকে। যে-দিকে জলের টান, জোয়ার-ভাটা,গোন-বেগোন। আমার নিজের সব জোরই যেন, ফুরিয়ে গেছে। ভেবেছিলাম, এ-জীবনে নিজের ইচ্ছের হাল ধরে বসে থাকব। দৈনন্দিনতার সংসার ভারের জলস্রোতে কখনো দিকভ্রষ্ট হব না। বুঝতে পাচ্ছি, আস্তে আস্তে জোর কমে আসছে মনের। শরীরেরও।
আশ্চর্য! এত অল্প দিনেই!
জীবনের, উৎসাহের, জীবনীশক্তির মোমবাতিকে আমি দু-দিকে জ্বালিয়েছিলাম। মোম যে এত দ্রুত পুড়ে যাবে, পুড়ে যাচ্ছে তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। যা-কিছু অনিষ্ট ছিল, জীবনের একে একে রুজির ডাস্টবিনে ধূলিমলিন, অদৃশ্য হয়েছে। অথচ, এ-জীবন থেকে পাওয়ার তেমন কিছুই নেই আমার। আরাম, আদর, যত্ন, ভালোবাসা, কোনো স্বার্থহীন নারীর কোমল নরম হাত। তাঁতের শাড়ি, নতুন গন্ধভরা কোনো কোল, মাথা-পেতে শোয়ার। পাওয়ার কিছুই নেই। শুধু কর্তব্য আছে, কাজ আছে, জেদ আছে, অর্থ নাম-যশ, আশা আকাঙ্ক্ষার জাঁতাকলে আটকা ইঁদুরের মতো আমি। অথচ আমার নিজের প্রয়োজন বলতে কতটুকু?
আমার ভবিষ্যৎ কী? যাদের ভবিষ্যৎ ভেবে সততই আমি চিন্তাকুল তারা আমার ভবিষ্যৎ নয়। বর্তমানও নয়। তবে কেন মরা? কেন অন্যের সুখের জন্যে এমন করে তিলে তিলে নিজেকে জ্ঞাতসারে ফুরিয়ে ফেলা? সংসারে আমার জন্যেই যদি আমাকে একজনমাত্র মানুষও না চেয়ে থাকে, তাহলে সেইসব তথাকথিত আপনজনদের জন্যে, ভালোবাসার জনদের জন্যে কেন এমন করে আত্মহত্যা করা? কেন-না, আমি বড়ো নরম বলে। বড়ো প্রাচীনপন্থী বলে। পরকে দুঃখ দিয়ে যে-সুখ পাওয়া যায়, সে-সুখ প্রত্যাখ্যান করেছি বলে।
কিন্তু পরকে দুঃখ না দিয়ে, কেউ কি সুখী হয়? কখনো কি হয়েছে? কোনোদিনও?
সুখ কাকে বলে জানি না।
যদিও অনেকই সুখ পেয়েছি–এত সুখ যে, লক্ষ লোকের ঈর্ষার কারণ হয়েছি। খাওয়ার সুখ, পরার সুখ, মনের সুখ, সম্মানের সুখ, অর্থের সুখ, নারী-শরীরের সুখ, ভালোবাসার সুখ। অথচ কোনো সুখেই মুখ গুঁজে থাকতে পারিনি বেশিক্ষণ।
কোনো সুখই সত্যিকারের সুখী করতে পারেনি আমাকে। এ, এক অভিশাপ!
সুখ যারে কয় সকল জনে বাজাই তারে ক্ষণে ক্ষণে
গভীর সুরে চাইনে চাইনে, বাজে অবিশ্রাম।
অর্থ পেয়ে ছুঁড়ে ফেলেছি। যশ পেয়ে, পায়ে মাড়িয়েছি। ভালোবাসার থরথর নারীশরীরে পুরুষালি নম্র প্রচন্ডতায় প্রবেশ করে দ্রুতগতিতে ফিরে এসেছি। কখনো বিরক্তির সঙ্গেও। নতুন করে, নতুনতর করে সুখকে প্রতিমুহূর্ত আবিষ্কার করার, ধরে রাখার চেষ্টা করেছি। চেষ্টা করে, হতাশ হয়েছি। হতাশ হতে হতে আবারও আশা রেখেছি। আশা করে, হতাশ হয়েছি। তারপর আবারও আশা করেছি।
এই অনুভূতিতে আমি কি একা? আমরা কেউই কি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে জেনেছি? জেনেছি, সুখের প্রকৃতিকে? আশা-হতাশার প্রকৃত তাৎপর্যকে? জীবনের গন্তব্যকে? কেউই কি জেনেছি?
অন্যের কথা জানি না। নিজের কথাই বলতে পারি শুধু, প্রতিমুহূর্তে, প্রতিক্ষণে নিজেকে নতুন করে জানছি, ভাঙছি, গড়ছি, নষ্ট করছি, অপবিত্র করছি, পরমুহূর্তেই আবার পবিত্র করছি, আর এমনি করে নিজেকে জানতে জানতে, ভাঙতে ভাঙতে ভুলের মধ্যে দিয়ে সত্যকে, আলোর দিকে ধাবমান শিশুর মতো টালমাটাল পায়ে ছুটে চলেছি।
এই ছোটা, দলছুটের ছোটা। এ-ছোটার কোনো তাৎপর্য নেই। তাৎপর্য বোধ হয় এইটুকুই যে, নিজেকে জানতে জানতে তাঁকেই জানার চেষ্টা করেছি।
আপনাকে এই জানা আমার ফুরাবে না, আমার ফুরাবে না, সেই জানারই সঙ্গে সঙ্গে তোমায় চেনা।