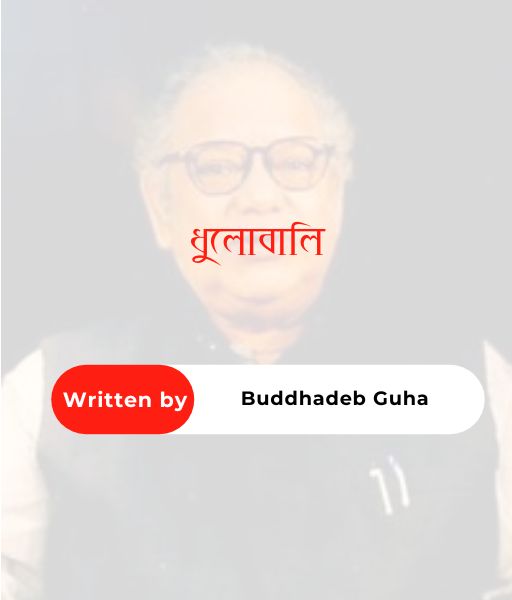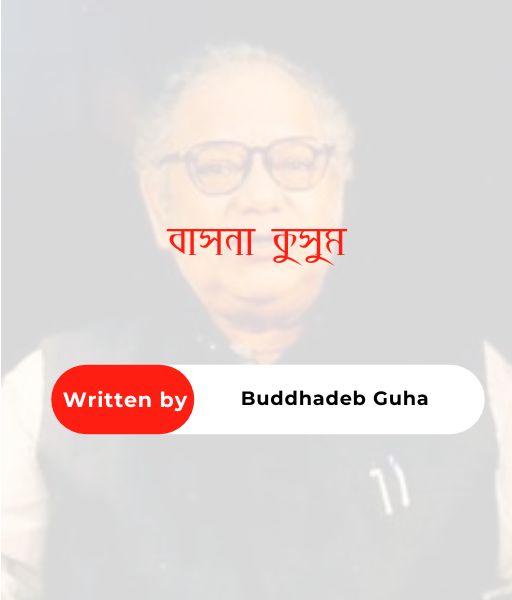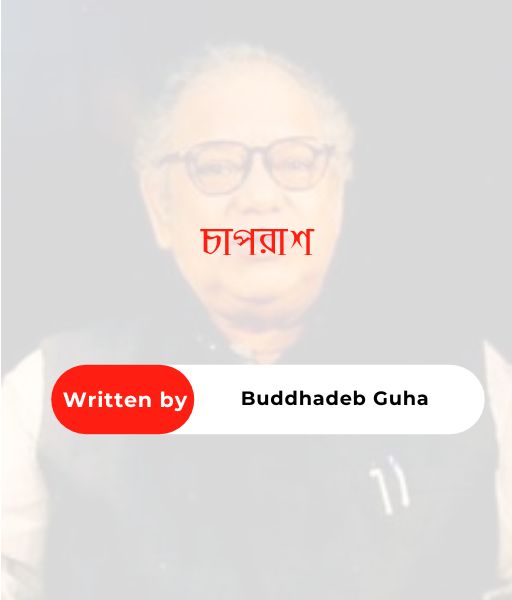ফ্ল্যাটের বসবার ঘরে
০৩.
ফ্ল্যাটের বসবার ঘরের প্রকান্ড কাঁচমোড়া জানলা দিয়ে চোখে পড়ে একটা বিরাট গাছ। শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে এই পাঁচতলা অ্যাপার্টমেন্টের লোকাল গার্জেনের মতো ঝুঁকে পড়ে এর রক্ষণাবেক্ষণ করছে যেন।
বড়ো গাছমাত্রই প্রতিষ্ঠান বিশেষ। এই কুয়াশা-ভেজা দূর দেশের গাছ আর আমাদের দেশের গাছের চেহারায় অমিল থাকলেও চরিত্রে কোনোই অমিল নেই। সেই কোটর, পাখি, লতিয়ে-ওঠা পরনির্ভর লতা, পাতা-ওঠা, পাতা-মরা, সেই তারুণ্য ও বার্ধক্যর আশ্চর্য অভিব্যক্তি এই গাছেও।
সেদিন খুব ভোরে উঠে জানলার পর্দা সরিয়ে তার পাশে বসে বাইরে চেয়ে অনেকদিন পর এক প্রভাতি পরজ মানসিকতার মধ্যে অনেকানেক কথা মনে আসছিল। ওই গাছে-বসা ও উড়ে-যাওয়া পাখিদের মতো আমার ভাবনাগুলোও আসা-যাওয়া করছিল।
মনে হচ্ছিল, পৃথিবীতে এখনও অনেক আশা আছে। দূরত্ব, কোনো দূরত্বই প্রকৃতিকে তেমন করে পৃথক করতে পারেনি। পারেনি মানুষকেও। বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের ভাষা ভিন্ন হয়েছে, এই পাখিদের ডাকেরই মতো, পোশাক বিভিন্ন হয়েছে এই পাখিদেরই পালকের মতো কিন্তু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে, মননের অধিকারে এবং মনুষ্যত্বের মূল পরিচয়ে এই বিপুলা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত গাঁথা রয়েছে একমালায়। যে-মালা মানুষ-সত্যর মালা। সে-সত্যর ওপর আর কোনো সত্য নেই। আর প্রকৃতি, তার গাছ-পালা, পাহাড়-নদী আকাশ-বাতাস সমেত এই পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে তাঁর অসীম অনন্ত অশেষ সত্তার প্রসন্ন ও বিরূপ প্রকাশে প্রকাশিত হয়ে আমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছেন বারে বারে যে, একই অখন্ড অনন্তের মধ্যে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা নিঃশ্বাস-ফেলা ও প্রশ্বাস-নেওয়া অদূরদৃষ্টিসম্পন্ন দাম্ভিক কীট আমরা। আমরা পথ, রথ ও মূর্তিকে দামি ভেবে নিয়ে আমাদের বুকের ভেতরের ন্যক্কারজনক, নুজ আত্মমগ্নতায় নিমজ্জিত থেকে অন্যক্ষেত্রে নিজেদেরই দেব বলে মনে করছি।
কুয়াশা-ভেজা আলতো-সবুজ আদুরে-নরম ঘাসে ঘাসে ভরা এই প্রান্তর, তার ওপরে চরে বেড়ানো নানা-রঙা টাট্ট-ঘোড়া, পাখির ডাকের সঙ্গে মিশে যাওয়া তাদের হে রব, প্রথম প্রবাসের ভোরের কুয়াশার গন্ধ, সব মিলিয়ে এই নিরিবিলি সকালে বড়ো একটা নিষ্পাপ দাবি-দাওয়াহীন আনন্দে আমার মনটা ভরে দিয়েছে। এমন আনন্দ হঠাৎ-হঠাৎ কিন্তু ক্কচিৎ অনুভব করা যায়। এ ভারি একটা গভীর আনন্দ, নিছক বেঁচে থাকার আনন্দ, চোখে দেখতে পাওয়ার আনন্দ, নাকের ঘ্রাণের আনন্দ ও সবচেয়ে বড়ো এক গা-শিরশির করা কৃতজ্ঞতার আনন্দ।
এই কৃতজ্ঞতা কার কাছে জানি না। কিন্তু এই কৃতজ্ঞতা বোধটা যে সত্যি সেকথা জানি। এই ক্ষণিক কৃতজ্ঞতার বোধের মধ্যে দিয়ে আমার মতো কতশত পাপী-তাপী মানুষ যে উত্তরণের সোনার দরজায় পৌঁছে যাচ্ছে প্রতিমুহূর্তে তা কে জানে? একজন নিশ্চয়ই জানেন। আর কেউ জানুন আর নাই-ই জানুন।
স্মিতা ঘরে এসে বলল, কী ব্যাপার? এত সকাল সকাল রবিরার ভোরে?
আমি বললাম, ক-টা দিনই বা আছি এখানে? যে-কটা দিন আছি, ভালো করে তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছি। বেশি ঘুমিয়ে কী হবে?
চা খেয়েছ?
না।
দাঁড়াও, করে আনছি।
ঘর থেকে চলে যাবার সময়ে স্মিতার ঠোঁটের কোণে একটু মৃদু হাসি ফুটে উঠল।
বুঝলাম ঠোঁট বলছে, ভাসুর আমার বড়ো কুঁড়ে।
আসলে, এখানে আসা-ইস্তক স্মিতা আমাকে রান্নাঘরে নিয়ে গিয়ে ভালো করে সব ট্রেনিং ট্রেনিং দিয়ে দিয়েছিল। সত্যি কথা বলতে কী, দেশ থেকে বিদেশের আত্মীয়-স্বজন বন্ধু বান্ধবরা হাত পুড়িয়ে রান্না করে খাচ্ছে বলে আমাদের যে একটা ধারণা বরাবরই থাকে সেটা পুরোপুরি ভুল। এখানে রান্না করাটা আর রান্নাঘরে সময় কাটানো একটা আনন্দ বই নয়। এত সুন্দর সব বন্দোবস্ত, এত চমৎকার বহুবর্ণ বাসনপত্র, এবং কিচেন প্যানট্রির সাজ-সরঞ্জাম যে রান্না করতে সকলেরই ইচ্ছে করে।
একথা এই ভরসায় বলছি যে, এই অপদার্থ যে নিজে কুল্লে শুধু চা, ওমলেট এবং তেঁতুলের মধ্যে লেবুপাতা কাঁচালঙ্কা ফেলে ডলে-টলে নিয়ে বানানো দারুণ একটা শরবত ছাড়া কিছুই বানানো জানে না সেই তারও যখন রাঁধবার শখ হয়, তখন অন্য অনেকেরই বিলক্ষণ হবে।
এখানে চা বানানো একটা ব্যাপারই নয়। হিটারের ওপর সুন্দর কেটলিতে প্যানট্রির বেসিনের কল থেকে জল ভরে নিয়ে চাপিয়ে দিলেই হল। হাই করে দিলে, কিচেন থেকে বেরিয়ে একবার বসার ঘরে দাঁড়ালেই শোনা যাবে কেটলির জল ডাকতে শুরু করেছে। তখন ফিরে গিয়ে একটা করে টি-ব্যাগ সুতো ধরে কাপের মধ্যে ফেলে জল ঢাললেই চা। তারপর দুধ চিনি মিশিয়ে নিলেই হল।
কিন্তু আমার ভাদ্রবউ বড়ো ভালো। লানডানে থেকেও সে আমাকে একেবারে প্রাগৈতিহাসিক বাঙালি যৌথ-পরিবারের ভাসুরের মতো যত্ন-আত্তি করছে। পান থেকে চুনটি খসবার জো-টি নেই। ওদের সময় ও অবকাশ এতই অল্প এবং সেই অবকাশে এত কিছু করবার থাকে যে, তার মধ্যে অতিথি সেবা করা সত্যিই মুশকিল।
আমার পক্ষে উচিত ছিল যে ওদের বাসন-টাসন ধুয়ে অথবা অন্যান্য নানা ব্যাপারে ওদের একটু সাহায্য করা। সাহায্য যে করিনি এ নিয়ে আমার ভায়া শোবার ঘরের বন্ধ দরজার আড়ালে ভ্রাতৃবধূকে এই ইনকনসিডারেট দাদা সম্বন্ধে কিছু বলেছে কি বলেনি তা ভায়াই জানে।
কিন্তু বলে থাকলেও, দাদার চরিত্রের যে কিছুমাত্র পরিবর্তন সাধিত হত, তা দাদার মনে হয় না। আমার মতো কুঁড়ে ও আরামি লোক বাংলাদেশেও পাওয়া মুশকিল। হালের বাংলাদেশ নয়। পুরোনো পুরো বাংলার কথা বলছি। এই ব্যাপারে ছোটোবেলায় আমার অনুপ্রেরণা ছিলেন আমার এক বন্ধুর দাদামশায়। তিনি লাইব্রেরি ঘরে বই পড়তে পড়তে গড়গড়া খেতেন। কখনো যদি গড়াগড়ার নল অন্যমনস্কতার কারণে হস্তচ্যুত হত, তাহলে তিনি তা কখনো নিজে হাতে তুলতেন না। পুরো নাম ধরে কোনো খিদমদগারকে ডাকতেও তাঁর অত্যন্ত পরিশ্রম বোধ হত। এমনকি কে আছিসরে-এত বড়ো একটা বাক্য বলার নিষ্প্রয়োজনীয় মেহনতও তাঁকে কখনো করতে দেখিনি।
অন্যমনস্কতা ও কুঁড়েমিরও একটা দারুণ নেশা আছে। রইসিও আছে। সেই নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তিনি যেন দূর জগৎ থেকে ডাক দিতেন–রে। শুধু রে।কে রে পর্যন্ত নয়।
ডাকামাত্র কেউ-না-কেউ দৌড়ে এসে তাড়াতাড়ি গড়গড়ার নলটা তুলে দিত তাঁর হাতে। নলটা আঙুলের মধ্যে পুনঃপ্রবেশ করার ঘটনাটাও তাঁর স্বর্গীয় আলস্য ও উদাসীনতাকে কিঞ্চিত্মাত্র ব্যাহত করত না। কিছুক্ষণ পর শব্দ শোনা যেত আবার ভুড়ুক ভুড়ক। খোলা দরজা দিয়ে এসে সারাবারান্দা ভরে দিত অম্বুরী তামাকের গন্ধ।
আমি তো দীনাতিদীন! বাঘা বাঘা লোকেরাও এই আলস্যর জয়-জয়কার করেছেন। বাট্রাণ্ড রাসেল তাঁর ইন প্রেইজ অফ আয়ডনেস বইয়ে কেমন যুক্তি-তক্কো দিয়ে ব্যাপারটার গুণাবলি বুঝিয়েছেন।
স্মিতা চা এনে দিয়েছিল।
আমি সবুজ মাঠে সম্পূর্ণ বিনা কারণে লক্ষমান ঘোড়াগুলোর দিকে চেয়ে চা খেতে খেতে আলসেমির চূড়ান্ত করছিলাম।
এখানের সবুজের সঙ্গে আমাদের দেশি মাঠঘাটের সবুজের তফাত আছে। ভালো করে কালি দিয়ে পালিশ-করা কালো চামড়ার জুতো আর কালো ক্যাম্বিসের জুতোর রঙে যে তফাত এই সবুজ ঔজ্জ্বল্যের তফাত অনেকটা সেরকম। তবে ম্যাটমেটে নয় ঠিক রংটা। ইংরেজি লাশ গ্রিন শব্দটাই এই সবুজত্বের একমাত্র অভিব্যক্তি। এ সবুজটা কেমন যেন নরম সবুজ, অনেকটা জাপানি চিত্রকরের ওয়াশের কাজের ছবির মতো ব্যাপারটা।
এই সবুজের বুকে লাফিয়ে-বেড়ানো টাটুঘোড়াগুলোকে দেখে মনে হয় ইংরেজি নার্সারি রাইমের ছবিওয়ালা বই থেকে সটান উঠে এসেছে ওরা। যে সব বইয়ে
রিঙ্গা রিঙ্গা রোজেস,
পকেটফুল অফ পোজেস
ইত্যাদি কবিতা ছাপা থাকে।
নার্সারি রাইমের কথা মনে হওয়ায় আমিও প্রায় ছোটোবেলায় ফিরে গেছিলাম, এমন সময়ে টবী উঠে এল এঘরে।
বলল, গুডমর্নিং রুদ্রদা। জানলার সামনে কী করছ?
আমি বললাম, এটা কী গাছ রে?
টবী বলল, এটা একটা গাছ।
কী গাছ?
টবী বলল, খী খারবার! আমি কি কবরেজ নাকি? গাছ-পাতা এসব চিনি না। গাছ; ব্যাস গাছ। পারোও বাবা তুমি।
তারপরই টবী বলল, প্রেমের গল্পে গাছের কোনো ভূমিকা আছে?
আমি চমকে উঠলাম। প্রথমে ভয় পেলাম, তারপর সপ্রতিভ গলায় বললাম নিশ্চয়ই আছে।
টবী অনেকক্ষণ একদৃষ্টে আমার দিকে পুরু লেন্সের চশমার মধ্যে দিয়ে চেয়ে থাকল। একটা হাই তুলল মস্ত বড়া। রাতে বোধহয় আমার ভাদ্রবউকে খুব আদর-টাদর করেছে।
তারপর একেবারে হঠাৎই বলল, তোমার গল্পের নায়করা গাছে ঝোলে গলায় দড়ি দিয়ে?
আমি অত্যন্ত বিপন্ন মুখে টবীর দিকে চেয়ে রইলাম।
ম্যাদামারা বাংলা সাহিত্যের প্রতীক এক ম্যাদামারা প্রেমের গল্প-নিকিয়ের কপালে যে এমন বিপদও লেখা ছিল তা কি আমি জানতাম?
আসলে শুধু টবী নয়, গাছগাছালি সম্বন্ধে খুব কম লোকেরই আগ্রহ থাকে। জীবনের অন্যান্য অনেকানেক ক্ষেত্রে অসম্ভব কৃতী লোকদেরও এ বিষয়ে উদাসীনতা আমাকে প্রায়শই মর্মাহত করে। কিন্তু জীবনে মর্মাহত হবার এতরকম কারণ থাকে যে, গাছগাছালির কারণে বেশিক্ষণ মর্মাহত হয়ে থাকা যায় না।
লানডানের টিউব ট্রেন যেখানে মাটির ওপর দিয়ে গেছে সেখানেই অনেক জায়গায় চোখে পড়ে ম্যালাস্কিগঞ্জে শীতকালে ফুটে-থাকা হলুদ ফুলের মতো ফুলের ঝোঁপ। অসংখ্য ফুল ফুটে আছে এখানে ওখানে। এখানে এ ফুলগুলোকে কী বলে, তা জানি না। টবীর বাড়ির পাশের বড়ো গাছটার নামও জানি না। জানতে পেলে খুশি হতাম। অবশ্য পৃথিবীর তাবৎ গাছের নাম যাঁরা জানেন, তাঁরা উদ্ভিদবিজ্ঞানী। যাঁরা নাম-না-জেনেও তাবৎ গাছপালা ফুল লতাকে ভালোবাসেন তাঁরা কবি। তফাত হয়তো এইখানেই; এইটুকুই।
পথের পাশে খয়েরি ও গাঢ় লাল ওয়াইল্ড-বেরির ঝোপে ঝোপে ডালগুলো ভরে আছে। আমাদের কুমায়ু পাহাড়ের কাউফলের মতো। পাশে পাশে নুয়ে আছে উইপিং-উইলো। উইলো গাছদের দাঁড়িয়ে থাকা আর নুয়ে-পড়ার হালকা আলতো ভঙ্গির মধ্যে বড়ো একটা নারীসুলভ কমনীয়তা আছে। গা ঘেঁষে দাঁড়াতে ইচ্ছে যায়। ভালো লাগে।
ততক্ষণে দু-কাপ কফি খেয়ে ভায়া আমার মুডে এসেছিল।
বলল, এসব লেখক-ফেখক লোকদের বেশিক্ষণ একা থাকতে দিয়ো না স্মিতা। তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও, চলো বেরিয়ে পড়া যাক।
শুধোলাম, কোথায়?
যেখানে দু-চোখ যায়।
তারপর একটু ভেবে বলল, কোথায় যাবে এল? চলো স্ট্র্যাট-ফোর্ড-অন-অ্যাভন-এ ঘুরিয়ে আনি।
বললাম, তা মন্দ হয় না, শেক্সপিয়রের জন্মস্থান। না গেলে জংলিপনা হয়।
টবী বলল, শেক্সপিয়র? সেডা আবার কেডা?
বললাম, তা জানি না, ছোটোবেলায়, কট্টর বাংলা ভাষায় লেখা এক প্রবন্ধে পড়েছিলাম, শেক্ষপিয়র এবং মোক্ষমুলার।
স্মিতা হেসে উঠে বলল, মোক্ষমুলার কী?
আমি উত্তর দেবার আগেই টবী বলল, বুঝেছি, ম্যাক্সমুলার।
তারপর বলল, জ্বালালে দেখছি।
স্ট্রাটফোর্ড-অন-অ্যাভন মিডেকস থেকে ঠিক কত দূর এখন আমার মনে নেই। তবে গাড়িতে বেশ কিছুটা পথ।
পরিজ, জোড়া-ডিম, তামাটে কড়কড়ে-চুরমুরে করে বেকন ভাজা, একেবারে ক্রিসপ টোস্ট। তার ওপর সদয় হাতে মাখন মার্গারিন ও মধু মাখিয়ে জমজমাট খেয়ে উঠলাম। পুরোপুরি ইংরিজি কায়দায়।
স্মিতা বলল, কটেজ-চিজ আছে। খাবে রুদ্রদা?
আমি বললাম, না। ভালো লাগে না।
টবী বলল সে কী? কটেজ-চিজ ভালো লাগে না কীরকম? আমরা তো প্রতিবার দেশে ফেরার সময় সকলেই এই অনুরোধ করে যে, একটু কটেজ-চিজ নিয়ে এসো।
স্মিতা বলল, কেন? ভালো লাগে না কেন?
বললাম, গন্ধ লাগে। আমার মনে হয় বেশি চিজ খেয়ে খেয়েই সাহেবদের গায়ে বোকা পাঁঠার মতো গন্ধ হয়।
স্মিতা হাসল। বলল, মোটেই নয়।
টবী বলল, অবজেকশান। তুমি সাহেবদের গায়ের গন্ধ শুকলে কবে? আমার গায়ে তো শুনি লেবুপাতারই গন্ধ।
স্মিতা রাগের হাসি হেসে বলল, তোমায় কে বলেছে?
তুমিই বলেছ। আবার কে বলবে?
এত অসভ্য না!
বলেই ধরা-পড়া মুখে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল স্মিতা, তৈরি হয়ে নিতে।
রবিবারের বাজার। ডাঁই-করা খবরের কাগজ ঘরের মধ্যে। রবিবাসরীয় সংখ্যা যে কী জিনিস নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস হয় না। আগে যখন এখনকার থেকেও আমার বুদ্ধি কম ছিল তখন ভাবতাম যে, সায়েবরা কত পড়ে। যে জাত একরবিবারেই হাজার পাতা কাগজ পড়ে শেষ করে দেয়, সে-জাত পৃথিবীময় প্রতাপ খাটাবে না তো কারা খাটাবে?
এখানে এসে এদের কায়দাটা জানা গেল। একটা কাগজের রবিবাসরীয় সংখ্যায় তো থাকবে না এমন জিনিস নেই। ধরা যাক বিশেষ সংখ্যাটি পঞ্চাশ পাতার। তার মধ্যে সাহিত্য, গান-বাজনা, মারধর, গোয়েন্দা-গল্প, রোমাঞ্চ গল্প, শ্লীলতাহানির বিবরণ, বিজ্ঞাপন, সিনেমা, ফুটবল, জাজ-মিউজিক, হিপিদের হিক্কাধ্বনি, এ-হেন বিষয় নেই যে নেই। সায়েবরা জমিয়ে ব্রেকফাস্ট ট্রেকফাস্ট খেয়ে কাগজের পাতায় পাতায় চোখ দুটোকে ফড়িং-এর মতো নাচানাচি করিয়ে কিছুক্ষণ পরেই নামিয়ে রেখে দেবেন। কেউ কেউ নিশ্চয়ই বেশিক্ষণও পড়বেন, কিন্তু শুধুই নিজের ভালোলাগার বিষয়টুকুই। স্বাভাবিক। কেউ দেখবেন সিনেমার পাতা, কেউ খেলা।
টবী টেলিভিশান খুলল। এখানে প্রায় সকলেরই রঙিন টেলিভিশান। শীতের দেশে টেলিভিশনের গুণের তুলনা নেই। কিন্তু আমাদের দেশে টেলিভিশান লোকের ভালো যেমন করবে খারাপও করবে। ছেলে-মেয়েদের পড়াশুনোর বিঘ্ন ঘটবে, এবং অনেকেরই মেদবৃদ্ধি, গেঁটে বাত এবং আরথ্রাইটিস হবে ঘরে বসে।
এইসব দেশে সন্ধের পর এত ঠাণ্ডা লাগে যে, বাইরে বেরিয়ে পায়জামা আর ফিনফিনে পাঞ্জাবির সঙ্গে চটি ফটাস ফটাস করতে করতে দু-খিলি অ-খয়েরি গুণ্ডিমোহিনী পান মুখে ফেলে যে অফিস থেকে ফিরে পথেঘাটে একটু সুন্দর মুখটুখ দেখে বেড়াবেন কেউ, সে উপায়টি নেই। বেঁচে থাকুক আমার দেশ। এদেশে ঘরের মধ্যে কুঁকড়ে-বসে টেলিভিশন দেখা ছাড়া আর কী করার আছে?
সামনেই ইংল্যাণ্ডের সাধারণ নির্বাচন।
টেলিভিশনে মি. হ্যাঁরল্ড ইউলসন, ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী নিজের দলের বক্তব্য রাখলেন, তারপই মি. এডওয়ার্ড হিথ তাঁর দলের বক্তব্য রাখলেন।
হ্যারল্ড উইলসন ভদ্রলোকের বহুদিনের অ্যাডমায়ারার আমি। ভালো লাগে, তাঁর বাগ্মিতা, বুদ্ধিমত্তা, রসবোধ। তাঁর বুদ্ধিমাজা পাইপ-খেকো চেহারারও ভক্ত আমি খুব।
কিন্তু টবী বলল, সাধারণ ইংরেজের ধারণা এই-ই যে, এবার মি. উইলসনের দল জিতলে সর্বনাশ হয়ে যাবে, কারণ মি. উইলসন সাহেবের দয়ামায়ায় দেশের সমূহ ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে। উৎপাদনে ব্যাঘাত ঘটছে, চাকরি-বাকরির অভাব; প্রচন্ড মুদ্রাস্ফীতি। সাধারণ ইংরেজ নাকি আর পারছে না। এবারে মি. ইউলসনের দলের জারি-জুরি নাকি আর চলবে না।
টবীর কথা যে ভুল তা প্রমাণ করে মি. উইলসনই পুনর্বহাল হয়েছিলেন আমি ক্যানাডায় থাকাকালীন, কিছুদিন পরই। তাঁর দলই জিতল।
মি. উইলসন সম্বন্ধে একটা গল্প শুনেছিলাম একজন ভারতীয়র কাছে, ভিক্টোরিয়া স্টেশানে; ডেভারের ট্রেনের জন্যে অপেক্ষা করতে করতে। মি. উইলসনের গাড়ি ট্রাফিক পুলিশের আলো অমান্য করেছিল বলে পুলিশ টিকিট দিয়েছিল তাঁকে। পরদিন কোর্টে গিয়ে জরিমানা দিয়েছিলেন তিনি। গণতন্ত্রে এবং প্রকৃত গণতন্ত্রে নাকি এমনই হওয়ার কথা!–সেই ভারতীয় বলছিলেন ওখানে নাকি অমনই হয়। সেটাই নাকি নিয়ম। এই আমি সেই গল্প শুনে অন্যমনস্ক হয়ে ভাবছিলাম, আমাদের দেশে তো প্রধানন্ত্রী বড়ো কথা, রাজ্যের ছোটোখাটো মন্ত্রীদেরই আইন অমান্য করার বহর দেখলে আমাদের লজ্জা হয়। আমাদের হয়, কিন্তু ওঁদের হয় না। স্বাধীনতোত্তর ভারতবর্ষে, লজ্জা থাকলে নেতা হওয়া যায় না।
প্রধানমন্ত্রী কলকাতা এলে বাস ট্রাম প্রাইভেট গাড়ির যাত্রীদের কপালে বহুদুর্ভোগ লেখা থাকে। আমার দেশে আইনের যাঁরা প্রকাশক তাঁরাই সবচেয়ে বেশি আইন ভাঙেন। পুলিশের গাড়ি যেখানে সবচেয়ে বেশি ট্রাফিক রুলস লঙ্ঘন করে, সরকারের সঙ্গে কোনোমতে যুক্ত থাকলেই যে দেশে আইন-শৃঙ্খলাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখানো যায়–সেই আশ্চর্য স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক দেশের স্তব্ধ ও মূঢ় নাগরিক হয়ে, ইংল্যাণ্ডের গণতন্ত্রের রকম দেখে সত্যিই মুগ্ধ হতে হয়। কবে যে আমাদের দেশেও ভোটের চেয়ে দেশসেবা বড়ো হবে, গদির চেয়ে আন্তরিকতা ও সততা উচ্চতার আসনে বসবে কে জানে? যাঁরা ভোট পান তাঁরা কবে ভোটদাঁতের সেবক বলে ভাবতে শিখবেন? কবে? আমাদের জীবদ্দশায় তা কি দেখতে পারব? নাকি এ জীবন এই হাস্যোদ্দীপক, ন্যক্কারজনক, দুঃখময় ভোটরঙ্গ দেখেই কেটে যাবে?
স্মিতা সেজেগুজে বেরিয়ে বলল, চলো। আমার হয়ে গেছে। ফ্ল্যাট বন্ধ করার আগে, ব্যাগের মধ্যে স্যাণ্ডউইচ বানিয়ে ভরে নিল। আপেল নিল ক-টা। বলল, অ্যাভন নদীর পাশে বসে গাছতলায় রাজহাঁসের সাঁতার কাটা দেখতে দেখতে লাঞ্চ খাব আমরা এই দিয়ে।
টবী বলল, সর্বনাশ করেছে! তুমি দেখি কবির মতো কথা বলতে আরম্ভ করলে?
স্বাভাবিক। আমি বললাম।
লিফটে ঢুকতে ঢুকতে টবী বলল, কেন? স্বাভাবিক কেন?
বললাম, উদ্ভিদবিজ্ঞানে একটা কথা আছে শুনেছি, অ্যাকোয়ার্ড ক্যারেকটারিস্টিকস। –মানে তুই যদি একটা কলাগাছকে আনারসের বনের মধ্যে পুঁতে দিস তাহলে দেখবি বছর। কয়েক বাদে কলাগাছের পাতাগুলো প্রায় আনারসের পাতার মতো চেরা-চেরা হয়ে যাচ্ছে।
টবী হো হো করে হাসল।
বলল, খী-খারবার।
তারপরই বলল, কী বুঝলে স্মিতা? বুঝলে কিছু?
স্মিতা বলল, হু।
টবী বলল, ঘোড়ার ডিম বুঝলে। গল্প-নিকিয়ে দাদার কায়দা বোঝোনি–ঘুরিয়ে তোমাকে কলাগাছ বলল।
কী খারাপ? বলে স্মিতা খুব গরম কফিতে আচমকা চুমুক দিয়ে ফেলার আওয়াজের মত একটা আওয়াজ করল।
আমি বললাম, যদি বলেই থাকি, তাহলেই বা আপত্তি কীসের? মাঙ্গলিক ব্যাপার রীতিমতো। কালিদাসের বর্ণনায় তো কদলীকান্ডবৎ ঊরু-টুরুর কথা লেখাই আছে। কলাগাছ কি খারাপ?
টবী গাড়ির দরজার লক খুলতে খুলতে বলল, খী-খারবার।
এ কীরকম ভাসুরঠাকুর? তুমি কি ভাদ্ৰবউ-এর ঊরু-টুরু এরই মধ্যে দেখে ফেলেছ নাকি?
এবার আমি আর স্মিতা একইসঙ্গে বললাম, অ্যাই টবী! কী হচ্ছে কী?
টবী নির্বিকার।
বলল, আজ সকাল থেকে হাওয়াটা বড়ো কনকনে। গাড়ি অবধি এসে পৌঁছোতে পৌঁছোতে ঠাণ্ডা মেরে গেছি। সোয়েটারটাও ভীষণ পাতলা। তাই একটু উরু-টুরুর আলোচনা করে গা-গরম করছি এই-ই যা।
গাড়ির মধ্যে হিটার চালিয়ে দিল টবী।
হু-হু করে ছুটে চলল গাড়ি। সামনে মিয়া-বিবি। বিবির গায়ের সুন্দর পারফিউমের গন্ধে গাড়িটা ভরে আছে আর মিয়ার গায়ের নেবুপাতা গন্ধ।
পথের এপাশে অনেকগুলো লেন ওপাশে অনেকগুলো লেন। মুখোমুখি ধাক্কা লাগার কোনোই সম্ভাবনা নেই। যে-গাড়ি অপেক্ষাকৃত বেশি জোরে চলছে সে-গাড়ি সবচেয়ে বাঁ দিকের লেন দিয়ে যাবে। ইংল্যাণ্ডের পথের নিয়ম আমাদের দেশের মতো। রাইট-হ্যাণ্ড ড্রাইভ গাড়ি এবং কিপ টু দ্য লেফট নিয়ম। অ্যাসফাল্টের একটি লেন। বাঁ-দিকেও ওরকম আছে। একেবারে ডানদিকে পার্কিং-এর জন্যে বা থেমে থাকার জন্যে। এখানে বলে সফট শোল্ডার। লেনগুলো সব কংক্রিটের। এক লেন থেকে আরেক লেন পৃথক করা হয়েছে আগাগোড়া মাইলের পর মাইল রাস্তায় সাদা দাগ দিয়ে। তার ওপরে ওপরে ক্যাটস-আই। রাতের বেলায় হেডলাইটের আলোয় জ্বলে।
হু-হু করে গাড়ি ছুটছে। গাড়ির কাঁচ তোলা বলে বাইরের দৃশ্য ছাড়া গন্ধ-স্পর্শ কিছুই পাবার জো নেই। এইদিক দিয়ে আমাদের দেশ বড়ো ভালো। কেমন কাঁচ নামিয়ে দিব্যি হাওয়া-বৃষ্টি খেতে খেতে যাওয়া যায়।
একটা কালো রোলস-রয়েস গাড়ি টবীর গাড়ির সামনে সামনে যাচ্ছিল। হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই–লেন চেঞ্জ করে বাঁ-পাশের লেন থেকে টবীর গাড়ি যে লেনে ছিল সেই লেনে এল।
হঠাৎ টবী হর্ন বাজাল, পিক। কিন্তু মাত্র একবারই বাজাল।
হর্ন বাজাতেই প্রথম খেয়াল হল যে, এতাবৎ এই স্লেচ্ছদের দেশে আসা ইস্তক একেবারেই গাড়ির হর্ন শুনিনি। ঠাণ্ডা দেশে এসে কানের কোনো গোলমাল হল কি না ভেবে দুশ্চিন্তায় পড়লাম। তারপর লাজলজ্জার মাথা খেয়ে বাঙাল দাদা তালেবর ভাইকে জিজ্ঞেসই করে ফেললাম, আচ্ছা, হর্নটা বাজালি কেন? তোর গাড়ির হর্নই শুনলাম। এতদিন খেয়াল করিনি একেবারেই যে, এখানের কোনো ড্রাইভার হর্ন বাজায় না।
টবী বলল, তুমি লক্ষ করেছ দেখছি। আসলে এখানে কোনো গাড়ি অন্য কোনো গাড়িকে উদ্দেশ করে হর্ন বাজানো মানে, তাকে বকে দেওয়া।
আমি বললাম, বলিস কী? বকে দেওয়া মানে?
মানে আর কী! অ্যাই চোপ, বোয়াদপ–গাড়ি চালাবার নিয়ম-কানুন না মেনে অসভ্যর মতো ইনকনসিডারেটের মতো গাড়ি চালাচ্ছ কেন?
এতক্ষণে মানে বুঝলাম।
এখানে আসার পর কনিসিডারেশন কথাটার মানে বুঝছি। সত্যি কথা বলতে কী, ইংরেজি অভিধানে যেসব কথা লেখা আছে সেগুলোর অনেকগুলোই ইংরেজদের কাছে শুধু কথামাত্র নয়–তার চেয়েও বেশি। এক-একটা কথার পেছনে ঐতিহ্যময় এক-একটা ইতিহাস আছে। সে ঐতিহ্য অবহেলা করার নয়, যে-জাত এত শো বছর তামাম দুনিয়ার ওপর ছড়ি ঘোরাল–সেই জাত আজকে গরিব এবং কোণঠাসা হয়ে যেতে পারে হয়তো কিন্তু অনেক কিছু শেখার আছে এখনও তাদের থেকে।
আমার বাবা বলতেন, পৃথিবীতে কোনো লোকই খারাপ নয়। খারাপ বলে কিছুই নেই দুনিয়ায়। যা খারাপতম, অন্ধকারতম যা; তারও একটা ভালো অথবা আলোকিত দিক থাকে। বলতেন, সবসময়ে সেই আলোকিত দিকটার দিকে তাকিয়ে থেকো–অন্ধকার দিকটাকে উপেক্ষা কোরো, তবেই বুঝতে পারবে এ পৃথিবীতে খারাপমানুষ কেউই নেই। খারাপ ব্যাপারও বেশি কিছু নেই।
বাবার এই দশলাখ টাকা দামি উপদেশ জীবনে কতটুকু কাজে লাগাতে পেরেছি জানি না, কিন্তু উপদেশটা মনে হয় একেবারে ফেলা যায়নি। নইলে যে জাত আমাদের এত বছর শুষে গেল, নেটিভ নিগার বলে গাল পাড়ল গাণ্ডেপিণ্ডে, সে জাতের ভালোটাই কেন চোখে পড়ে আগে? আগে আগে বইপত্রে যা পড়েছি তা পড়েছি; কিন্তু এখানে এসে বুঝতে পারছি প্রতিমুহূর্তে যে, গণতন্ত্র বলে যদি এখনও কিছু থেকে থাকে তবে তা সবচেয়ে বেশি আছে এই ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জেই। জানি যে, আছে কথাটা আপেক্ষিক। কানা-মামা নাই-মামার চেয়ে ভালো বলেই জেনে এসেছি চিরদিন। তাই বলতে হয়, আছেই। না থাকলে এত বছর অলিখিত সংবিধান নিয়ে এরা কেমন করে দিব্যি হেসেখেলে চালিয়ে গেল! ভদ্রতাও আছে, যা আমাদের এখনও শেখার!
আমরা স্বীকার করি আর নাই-ই করি এই ঠাণ্ডা দেশের লোকগুলোর গণতান্ত্রিক বিশ্বাস, আদালতের প্রতি সম্মানবোধ এবং আদালত ও প্রশাসনের মধ্যে ন্যায়সঙ্গত ও স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবধানকে মেনে চলার দৃষ্টান্ত অনেক দেশের সংবিধান রচয়িতাদেরই অনুপ্রাণিত করেছিল। তাই যখন দেখি যে অনেক দেশেই সংবিধানটা যেন বারোয়ারি হরিসভার চালাঘরের চাল হয়ে উঠেছে, যে পাচ্ছে, সে-ই একখাবলা খড় উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে উনোন ধরাচ্ছে, তখন ভারি আশ্চর্য ঠেকে।
স্মিতা হঠাৎ চিন্তার-জাল ছিঁড়ে দিয়ে বলল, চকোলেট খাবে রুদ্রদা?
আমি হাত বাড়িয়ে চকোলেট নিয়ে মুখে পুরে আবার ভাবতে লাগলাম–বাইরে তাকিয়ে।
স্মিতা মুখ ফিরিয়ে, যোগিনীর মতো শ্যাম্পু-করা চুল দুলিয়ে বলল, কী ভাবছ বলো না রুদ্রদা?
অনেকক্ষণ চুপ করে রইলাম আমি।
স্মিতা আবার বলল, বল না বাবা!
বাপীর সঙ্গে অনেকানেক ব্যাপার নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। আমার দেশের সঙ্গে এদেশের তুলনামূলক আলোচনা। মনটা খারাপ লাগে দেশের কথা ভাবলে। তখন কথা বলতে ইচ্ছে করে না। তবুও স্মিতার পীড়াপীড়িতে বললাম, অনেকদিন আগে আয়নার সামনে বলে একটা গল্প লিখেছিলাম আমি। সেই গল্পের যে নায়ক, তার বাবা ছিল জমিদার। আমাদের দেশের দশজন জমিদার যেমন হয়ে থাকে। বাবার মৃত্যুর পর সে সমবায়িক ভিত্তিতে তার সমস্ত জমি প্রজাদের সঙ্গে ভাগ করে নিয়ে একসঙ্গে চাষ করে ফসল ভাগ করে নিত সমান করে। তার ইচ্ছে ছিল, দেশের জন্যে অনেক কিছু করে, ভালোবাসত সে তার দেশকে; দেশের লোককে।
আমার গল্পের নায়ক, উত্তরপ্রদেশের ছেলে রাজির অনেক ভাবত-টাবত। তার বাবা যে জলসাঘরে বাইজি নাচাত সেই জলসাঘরে সে চারটে কালো অ্যালসেশিয়ান কুকুর পুষেছিল। একজনের নাম দিয়েছিল মালিক; অন্যজনের নোকর। আর দুজনের নাম দিয়েছিল আমির আর গরিব। এই চারটে কুকুরকে রাজিন্দর খাইয়ে রেখে, না-খাইয়ে রেখে নানাভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে কুকুরের বাচ্চাদের মধ্যে থেকে বাঘের বাচ্চার মতো নেতা জন্মায় কি না তাই দেখবার চেষ্টা করছিল।
স্মিতা আর টবী একসঙ্গে বলে উঠল এল না, তারপর কী হল তোমার গল্পের। নেতা জন্মাল?
আমি একটু চুপ করে থেকে বললাম, গল্পটা অনেক বড়ো। পুরোটা বলা যাবে না। বলে লাভও নেই।
স্মিতা বলল, তবুও এল। শেষে কী হল, বল।
আমি বললাম, শেষটা বলার মতো নয়।
তারপর বললাম, দেশকে ভালো-টালো বেসে দেশের লোককে ভাই-বিরাদর ভেবে শেষকালে রাজিন্দর বুঝতে পারল–ধীরে ধীরে বুঝল যে তা নয়, হঠাৎ ধাক্কা খেয়েই বুঝল যে, দেশকে ভালোবাসার মতো বোকামি আর নেই। বুঝল যে, কুকুরের বাচ্চাদের নেতা কখনোই বাঘের বাচ্চার মতো হয় না। একথা অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বুঝে রাজির সেই আমির, গরিব, নোকর ও মালিক চার কুকুরকেই গুলি করে মেরে ফেলে নিজেও আত্মহত্যা করে মরল। মরে যাবার আগে অত্যাচারী, প্রজার-ঘামে ফুর্তি ঝরানো, পায়রা-ওড়ানো জমিদার বাবার জলসাঘরের কাঁচের দেওয়ালে হাতাশার আলকাতরা দিয়ে লিখে গেল রাজিন্দর যে, কুকুরের বাচ্চাদের নেতা কখনোই বাঘের বাচ্চা হয় না।
স্মিতা বলল, ঈ-শ-শ-শ!
টবী বলল, খাসা গল্প তো! এমন গল্প বানাও কী করে? যাকগে, ছাড়ো তো দেখি! এই সামনেই একটা ভিলেজ-পাব আছে–চলো একটু বিয়ার খাওয়া যাক। তোমার গল্প শুনে তালু শুকিয়ে গেছে–অন্যসব দিশি লেখকদেরও কি তোমার মতো ভীমরতি ধরেছে নাকি? প্রেমের গল্প ছেড়ে এসব কী কুকুর-মেকুর নিয়ে লেখা? ছ্যা ছ্যা:!
আমি লজ্জা পেলাম।
হঠাৎ টবী বলল, এই যাঃ, তোমাকে বলতে ভুলে গেছিলাম আমাদের এপথে আসার সময়ে ইটন-এর রাস্তা দেখলে না? ইটন ইংল্যাণ্ডের সবচেয়ে নাম করা পালবিক স্কুল জানো?
বললাম, তাই তো শুনেছি।
স্মিতা বলল, কেন? হ্যারোও সেরকমই ভালো। লর্ড ফ্যামিলির ও পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো বড়ো ঘরের বড়ো বড়ো লোকের ছেলেরা এসব স্কুলে পড়ে। চিরদিন পড়েছে।
টবী শুধোল, আমাদের পন্ডিতজি যেন কোনটাতে লেখাপড়া করেছিলেন?
স্মিতা বলল, দুটোর মধ্যে একটাতে। কোনটাতে ঠিক মনে নেই।
স্মিতা বলল, ছাড়ো, সে কি আজকের কথা?
টবী গাড়িটা পথের ওপরের ছোটোখাটো পাবটার পাশে রাখল। লতানো জংলি গোলাপে ছেয়ে আছে দেওয়াল। কুঁড়ি ধরেছে লাজুকলাজুক। আরও নানারকম লতাতে সমস্ত সামনের দিকটা ছেয়ে আছে ছোটো সরাইখানার।
গাড়ি লক করে আমরা পাবের ভেতর ঢুকলাম। ভেতরে কুসুমগরম। আজ ছুটির দিন। এখানে ওখানে কিছু অল্পবয়েসি ছেলে জোট পাকিয়ে বসে, বিয়ার খাচ্ছে। মাঝ-বয়েসি একদল নারী-পুরুষ গোলটেবিলে জমিয়ে বসে পরনিন্দা-পরচর্চা করছে।
টবী বলল, জানো তো; ছোঁড়াগুলো মহাপাজি। বাড়িতে বউকে বলে আসবে ফুটবল খেলতে যাচ্ছি। ফুটবল খেলাটা ছুতো। বলের পেটে গোটাকয়েক এলপাথাড়ি লাথি মেরে গুচ্ছের বিয়ার গিলে দেরি করে বাড়ি ফিরে বউকে বলবে, বড়ো ক্লান্ত। খেলে এলাম।
স্মিতা বলল, আহা! কোন দেশের লোকে বউকে গুল না মারে?
টবী সঙ্গে সঙ্গে বলল, কেন? আমি মারি না।
স্মিতা হো-হো করে হেসে উঠল, তুমি আবার মারো না!
টবী কী যেন যেন একটা পানীয় নিল।
আমাকে বলল, কী খাবে তুমি?
আমি বললাম, তুই ত্রিফলা-ভেজানো জলের মতো দেখতে ওটা কী খাচ্ছিস?
টবী বলল, খী খারবার! ত্রিফলার জল কেন হবে, এটা এল!
সমারসেট মমের উপন্যাস কেকস অ্যাণ্ড এল-এ প্রথম এল-এর কথা পড়ি।
ভাবলাম, এই অভাগার কপালে যখন এল চাখবার সুযোগ এসেছে তখন চেখেই দেখা যাক।
আমি বললাম, আম্মো খাব।
তারপর বললাম, স্মিতা তুমি?
স্মিতা বলল, অ্যাপল জুস।
বললাম, তুমি এল খাও না? টবী তো মনে হচ্ছে ভালোবাসে।
স্মিতা অন্যদিকে তাকিয়ে বলল, শুধু এল কেন? ও তো এ থেকে জেড পর্যন্ত সব কিছুই ভালোবাসে।
আমি হাসলাম।
মুখের হাসি শুকোতে না শুকোতেই স্মিতা বলল, এতক্ষণ তো হ্যারো আর ইটনের গল্প খুব হল। তুমি কোন স্কুলে পড়তে রুদ্রদা?
আমি হ্যারো এবং ইটনের সঙ্গে একটুও পার্থক্য না রেখে একনিশ্বাসে বললাম, তীর্থপতি ইনস্টিটিউশান।
টবী ফিক করে হাসল। ওর মুখ চলকে এল গড়িয়ে পড়ল।
সঙ্গে সঙ্গে চট করে বিলিতি কায়দায় বলল, এক্সকিউজ মি!
আমি সোজা ওর চোখে তাকিয়ে বললাম, তোর হাসি দেখে মনে হচ্ছে তুইও বোধহয় ইটনে বা হ্যাঁরোতে পড়তিস? পড়তিস তো তুই চেতলা বয়েজ স্কুলে–সে কি আমার স্কুলের চেয়ে অনেক বেশি ভালো?
টবী তখনও হাসছিল।
বলল, তা নয়; তখন আমরা বলতাম :
যার নেই কোনো গতি।
সে যায় তীর্থপতি।
আমি বললাম, খবরদার স্কুল তুলে কথা বলবি না।
স্মিতা খিলখিল করে হাসছিল।
আমার খবরদার শুনে চারদিক থেকে অনেক মোটা-রোগা সাহেব-মেম ড্যাব ড্যাব করে। তাকাল আমার দিকে।
আমিও উলটে তাকালাম। মনে মনে বিড়বিড় করে বললাম, তোমাদের নিয়ম তোমাদের নিয়ম, আমাদেরটা আমাদের। তোমরা পাত্তারি গুটিয়ে চলে আসার পর আমরা যে কী জব্বর সায়েব হয়েছি তা যদি তোমরা একটিবার আমাদের দেশে গিয়ে দেখতে বাবুসায়েব তবে তোমাদের আত্মশ্লাঘার আর শেষ থাকত না। কিন্তু আমি তো বাঙাল। বাঙালই আছি। তোমরা ভুরুই কুঁচকোও আর যাই-ই করো।
আসলে সাহেব-মেমগুলো ভীতু হয়। চোখে চোখে কটমট করে তাকালে ভয় পেয়ে যায়। আফটার অল আমরা কাঁপালিকের দেশের লোক–চোখে চোখে চেয়ে ভস্ম করে দেওয়াই বা আশ্চর্যি কী?
ওরা একটু তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিল।
হঠাৎ আমি টবীকে শুধোলাম, আচ্ছা কাঁপালিকের ইংরিজি কী রে?
টবী কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল, তারপর উত্তর জানে না বলে বলল, একটু পরই তো শেকসপিয়রের বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছি, তাঁকেই জিজ্ঞেস কোরো না বাবা!
স্মিতাকে বললাম, আচ্ছা সাহেবদের গাত্রবর্ণের সঙ্গে সাঁতরাগাছির ওলের তুলনা কোথায় আছে বলতে পারো?
স্মিতার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।
বলল, দাঁড়ান দাঁড়ান; ভেবে নিই একটু।
পরমুহূর্তেই উত্তেজিত হয়ে বলল, প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর মহাস্থবির জাতক বইয়েতে পড়েছি।
আমি বললাম, সাব্বাস! জিতা রহো ভাদ্দরবউ!
সেই গাঁয়ের পাবটা থেকে বেরিয়ে কিছুক্ষণ আসার পরই অ্যাভন নদী পেরিয়ে এলাম আমরা। পেরিয়ে এসেই গাড়ি দাঁড় করাল টবী।
গাড়ি দাঁড় করাতে কম ঝামেলা পোয়াতে হল না। গাড়িতে গাড়িতে অর্থাৎ কারে কারে কারাক্কার। তিল ধারণের স্থান নেই।
ওঃ, বলতে ভুলে গেছিলাম, এখানে এসে পৌঁছোবার আগে টবী বাঙালকে হাইকোর্ট দেখাবার মতো পথিপার্শ্বে অক্সফোর্ডে নিয়ে গেছিল।
আমার, অন্যান্য অনেকানেক বাঙালের মতোই ধারণা ছিল অক্সফোর্ডও শান্তিনিকেতন কি বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো একটি সমৃদ্ধ ও একীভূত ব্যাপার। কিন্তু টবী যা বলল ও দেখাল তাতে দেখলাম বহু ছড়ানো-ছিটানো কলেজ। মানে একটি প্রকান্ড কলেজ-পাড়া। বহু পুরোনো সব স্যাঁতসেঁতে হিমকনকনে ইমারত। সঙ্গে হোস্টেল-টোস্টেল বা গির্জাটির্জাও আছে। এই সব বিভিন্ন কলেজ-ছাত্রাবাস ইত্যাদি অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি।
সত্যি কথা বলতে কী দেখে রীতিমতো হতাশ হলাম। কাশীর বিশ্বনাথের মন্দিরের ভেতরে যেমন একটা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভয় ভয় ভাব–এখানেও তেমন। পান্ডাদের অত্যাচার আছে কি নেই অত অল্প সময়ে বোঝা গেল না। তবে আমার যে পিসির মেজোজামাই অক্সফোর্ডের এম এ বলে আমাদের সঙ্গে ঠোঁট বেঁকিয়ে কথা বলে এসেছেন চিরটাকাল, এবং আমাদের মুনিষ্যি বলেই গণ্য করেননি, তাঁর প্রতি এক হঠাৎ-ধিক্কারে মনটা ছাতারে পাখির মতো ছ্যা: ছ্যা: করে উঠল।
অ্যাভন নদীটি বেশ। নদী বলা ঠিক নয়। আমাদের কলকাতার কেওড়াতলার গঙ্গার চেয়ে সামান্য চওড়া। তবে রূপটি ভারি শান্ত; স্নিগ্ধ।
টবী বলল, কেমন বুঝছ?
আমি বললাম, দারুণ।
কী দারুণ?
জায়গাটা।
লোকটাও দারুণ। স্মিতা বলল।
এমন জায়গায় না জন্মালে শেক্ষপিয়র যক্ষপিয়রও হতে পারতেন।
দুম করে টবী বলল।
আমি উত্তেজিত হয়ে বললাম, মুনি-ঋষিদের সম্বন্ধে এমন তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে কথা বলতে নেই।
টবী চটে গিয়ে বলল, কেন? নেই কেন? রবিঠাকুর জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে না জন্মে যদি কাকদ্বীপের কাঁকড়া-ধরা জেলের বাড়ি জন্মাতেন, তাহলে কি এই রবিঠাকুর হতেন?
স্মিতা কথা কেড়ে বলল, এই রবিঠাকুর না হলেও কাকদ্বীপের সেরা কবিয়াল যে হতেন সে বিষয়ে তোমার কোনো সন্দেহ আছে?
আমি চটে উঠে বললাম, তোরা থামবি? শেক্সপিয়রের বাড়ি কোনটা তা দেখাবি?
টবী দার্শনিকের মতো ঘুরে দাঁড়িয়ে হাওয়ায় থুতনি নাচিয়ে বলল, As you like it.
স্মিতা হেসে উঠল। বলল, বাঃ বাঃ, স্ক্র্যাট-ফোর্ড-অন-অ্যাভনে এসে একবারে শেক্সপিয়রি ভাষায় কথা বলতে শুরু করলে যে!
টবী অনাবিল ও সারল্যময় অজ্ঞানতার সঙ্গে বলল, মানে বুঝলাম না। স্মিতা আমার দিকে কটাক্ষে চেয়ে বলল, কান্ডটা দেখলে রুদ্রদা। বুঝতে পারছ কী অকালকুষ্মন্ডকে বিয়ে করেছি?
টবী সেই নিষ্পাপ মুখেই বলল, খী খারবার! এ কী হেঁয়ালি রে বাবা।
স্মিতা কিণ্ডারগার্টেন ক্লাসের দিদিমণির মতো গলায় বলল, As you like it, শেক্সপিয়রের একটি বইয়ের নাম।
টবী একটুও অপ্রতিভ না হয়ে বলল, অ! তুমি পড়েছ বুঝি? তা পড়ে থাকবে। সাহিত্যের ছাত্রী ছিলে তুমি। কিন্তু Break-even point? মানে, না তুমি বলতে পারো, না তুমি পড়েছ। নাকি তোমার শেক্ষপিয়রই পড়েছিলেন?
বলেই বলল, অমন তুচ্ছাতিতুচ্ছ কারণে লোককে হেয় কোরো না। সবাই সব জানে না।
আমি বললাম, এবারে কিন্তু সত্যিই তোরা ঝামেলা করছিস।
টবী কথা ঘুরিয়ে বলল, এসো, আমার সঙ্গে এসো। তোমাকে বাড়ি দেখাই।
কিন্তু সেই সরু রাস্তার ছোটোখাটো দোতলা কাঠের বাড়িতে ঢোকে কার সাধ্যি!
ট্যুরিস্ট বাসের পর ট্যুরিস্ট বাস দাঁড়িয়ে আছে। লম্বা লাইন পড়েছে দর্শনার্থীদের।
টবী বলল, দাঁড়িয়ে পড়ো লাইনে। এখানে ইট পাতার সিসটেম চালু হয়নি এখনও।
আমি বললাম, নাঃ।
টবী বলল, এই জন্যেই তোমাকে ভালো লাগে রুদ্রদা। এ কী আদিখ্যাতা এল দেখি! তিনি কোথায় শুতেন, কোথায় বসতেন, কোন বাথরুমে যেতেন এসব দেখবার জন্যে এই যে গুচ্ছের সব মোটা মেমসায়েব লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দেখছ তাদের বেশির ভাগের বিদ্যেই আমার মতো। তবু, শেক্সপিয়রের শোওয়ার ঘর না দেখলে যেন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত এদের। এও যেন নীলের ব্রত। না মানলে শাশুড়ি চটে যাবে। খী খারবার!
টবীর কথায় পুরোপুরি সায় না দিতে পারলেও একেবারে যে ওর কথা উড়িয়ে দেওয়ার তাও নয়। আমি অন্তত কখনো অমন বাথরুমে উঁকি দেওয়া ঔৎসুক্য বা ভক্তিতে বিশ্বাস করিনি। তার চেয়ে বরং চারপাশটা ঘুরে দেখা ভালো।
অ্যাভন নদীতে রাজহাঁস চরছিল। ছোটো ছোটো নৌকো ছিল চড়ার জন্যে। আজ থেকে বহুদিন আগের, শেক্সপিয়রের ছোটোবেলায় এই নদী, নদীর পারের উইলো গাছ এখন না দেখতে-পাওয়া উইণ্ডমিল সব কেমন ছিল তা কল্পনায় অনুমান করতে ভালো লাগে। এই ভালোলাগাটুকুই, পুরোনো অতীতের বেলজিয়ান কাঁচের আয়নার ভেঙে-যাওয়া টুকরো টুকরো কল্পনার আঠা দিয়ে জোড়া লাগিয়ে তাকে দেখতে যত সুন্দর লাগে, আজকের সস্তা কাঁচের বর্তমানে তাকাতে ততখানি সুন্দর আমার কখনোই লাগে না। হয়তো নগ্ন বর্তমানের চেয়ে অস্পষ্টতার কুয়াশা-ঘেরা অপ্রতীয়মান অতীতই আমার কাছে অনেক বেশি প্রিয় বলে।
তা ছাড়া সত্যি কথা বলতে কী, যদিও ভয়ে ভয়েই বলছি, শেক্সপিয়রকে আমি কখনোই রবিঠাকুর বা টলস্টয়ের সঙ্গে একাসনে বসাতে পারিনি। তিনি প্রকান্ড প্রতিভা ছিলেন সন্দেহ নেই। বহুমুখিনতা–তাতেও তাঁর জুড়ি পাওয়া ভার। কিন্তু যেহেতু আমরা ইংরেজশাসিত ছিলাম, সেইহেতু, ব্রিটিশ সার্জেন্ট-মেজর, স্কচ-হুঁইস্কি, কটেজ পিয়ানো গ্র্যাণ্ডফাদার ক্লক শেক্সপিয়রের চূড়ান্ত উৎকর্ষ সম্বন্ধে কারও কোনো দ্বিমত থাকতে পারে যে, একথা মনে করার মতো দুঃসাহস হয়তো আমাদের রক্তকণিকাতে কখনো সঞ্চারিত হয়নি।
আমার এই ধৃষ্টতায় যদি কোনো জ্ঞানীগুণী পাঠক ক্রুদ্ধ হন তাহলে পূর্বাহ্নেই মার্জনা চেয়ে নিচ্ছি। নিজগুণে তাঁরা মার্জনা করবেন আশা করি। যেটা বললাম, সেটা আমারই একান্ত মত। অর্বাচীন মূর্খের মতামতে পন্ডিতজনের উম্মার কারণ ঘটা উচিত নয়।
পথের দু-পাশে দোকান-পাট। ইংরেজ বেনেরা যেখানে পাচ্ছে বোকা ট্যুরিস্টদের পকেট কাটছে। এদের পকেট-কাটার নমুনা দেখে ইঁদুরের বালিশ ও কাগজ কাটার কথা মনে পড়ে যায়। ইঁদুরদের একটা দাঁত থাকে আত্মঘাতী দাঁত। প্রতিনিয়ত কাটাকুটি করে–সেই দাঁতকে তাদের ক্ষইয়ে ফেলতে হয়। নইলে সেই দাঁত তাদের মগজ ফুটো করে তাদের মরার পথ বাঁধিয়ে দেয়। অতএব প্রয়োজন থাকুক কি নাই-ই থাকুক, নিজেদের বেঁচে থাকার তাগিদে তাদের অবিরাম লেপ, তোষক এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা ইত্যাদি তাবৎ কাটিতব্য বস্তুকে কেটে যেতে হয়। ইংরেজদেরও বোধহয় এমন কোনো গুপ্ত দাঁত-টাঁত আছে। অন্যের পকেট অবিরাম না কাটলে তাদের মরার সময় যে ত্বরান্বিত হবে একথা তারা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমল থেকে জেনে এসেছে। এতএব ঘরে-বাইরে কুটুর কুটুর কেটে যাচ্ছে ইংরেজ। খিদে থাক আর নাই-ই থাক।
হঠাৎ আমার সামনে দিয়ে একজন সায়েব কার্জন-পার্কের কান পরিষ্কার করনেওয়ালা বাহাদুরদের মতো একটা থলে-মতো নিয়ে, ককনী ভাষায় কী যেন কঁকিয়ে কঁকিয়ে বলতে বলতে চলে গেল।
আমি থমকে পড়ে টবীকে শুধোলাম, কী ও? কীসের ফেরিওয়ালা? হজমিগুলির?
টবী হাসল।
বলল, ওরা কি সর্ষেবাটা দিয়ে ইলিশ খায়, না বিরিয়ানি পোলাউ? খায় তো আলুসেদ্ধ, কপিসেদ্ধ। তারই গালভরা নাম ডিনার। বদ-হজমের ব্যারাম এদের নেই। এ পোকা-মাকড়, তেলাপোকা মারার কোনো ওষুধ-টষুধ হবে।
আমি বললাম, আসার আগে আমার খেয়াল হয়নি একবারও নইলে পেটেন্ট অ্যাণ্ড ট্রেডমার্কের পৃথিবীখ্যাত স্পেশ্যালিস্টস ডি. পেনিং এণ্ড ডি. পেনিং-এর পার্টনার রবার্ট ডিপেনিংকে বলে সুনির্মল বসুর ছারপোকা মারার ওষুধটা পেটেন্ট করে নিতাম।
স্মিতা বলল, ওষুধটা কীরকম?
বললাম, ওষুধটা হোমিওপ্যাথির শিশিতে বিক্রি হত। লাল-নীল-ওষুধ। সঙ্গে ব্যবহার বিধিও লেখা থাকত। নাম ছিল, ছারপোকা বিধ্বংসী পাঁচন। সঙ্গে ব্যবহারবিধিও থাকত। তাতে লেখা থাকত, সাবধানে ছারপোকা ধরিয়া মুখ হাঁ করাইয়া একফোঁটা গিলাইয়া দিবেন। মৃত্যু অনিবার্য।
ভাদ্রবউ-এর ছুটি শেষ হয়ে গেছে।
টবী তাকে যে কর্তব্য দিয়েছিল তা সে সুষ্ঠুভাবে সমাধা করেছে। বাঙাল ভাসুরঠাকুরকে পথঘাট চিনিয়ে দিয়েছে, লানডানারদের রাহানসাহান খাল-খরিয়াৎ সমঝিয়ে দিয়েছে। এবার সে তার কমপিউটারের কাজে ফিরে গেছে।
অফিস যাওয়ার আগে সেদিন সে শুদ্ধ ও পরিমার্জিত বাংলায় যা বলল তা খারাপ ভাষায় তর্জমা করলে দাঁড়ায় যে টাটা-বাই-বাই, খোদার ষাঁড় এবার চরে-টরে খাও।
ফ্ল্যাটের একটা চাবি আমার কাছে আর একটা স্মিতা নিয়ে গেছে। টবী দেরিতে ফেরে। টবী ফেরার আগেই হয় আমি নয় স্মিতা ফিরে আসব বা আসবে।
টবী অফিস বেরোবার আগে ফিসফিস করে বলল, বেডরুমটা বন্ধ থাকবে তবে তোমার ঘর এবং ড্রইং রুম খোলা। ড্রইং রুমের মেঝেতে পুরু কার্পেট পাতা আছে–নরম সাদাটে সোনালি-রঙা বড়ো বড়ো রেশমি লোমওয়ালা ছাগলের চামড়াও পাতা আছে–তোমার শুধু কাউকে ধরে আনতে হবে। তারপর কোনোই কষ্ট হবে না। হাঁটু ছড়ে যাবার সম্ভাবনা নেই। ফার্স্ট ক্লাস বন্দোবস্ত।
আমি বোকার মতো হাসলাম।
আমার ভায়া তো জানে না যে আমার এলেম কতদূর। আমার সব গল্পের নায়কই একেবারে ওয়ার্থলেস। গল্পের নায়ক যখন নায়িকার বাড়ি যায় তখন নায়িকার স্বামী প্রায়শই অনুপস্থিত থকে। তবুও আমার নায়ক এমনই মরালিস্ট যে নায়িকার সুন্দর হাতে হাত রেখে নায়িকার বানানো চা শিঙাড়া-সহযোগে খেয়ে দুপুরবেলায় উদোম টাঁড়ে চড়ে বেড়ানো গরুর মতো প্রচন্ড শব্দ করে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে নায়িকার বাড়ি থেকে চলে আসে। আমার গল্পের নায়কদেরই যখন এতটুকু সাহস নেই তখন গল্পকারের সাহস যে কতটুকু তা তো গল্পকারই জানে।
ওরা চলে গেলে ধীরে সুস্থে চা করলাম। চা বানালাম বার দুই। একার জন্যে আর ব্রেকফাস্টের ঝামেলা করলাম না।
নর্থ ওল্ট টিউব স্টেশান থেকে পিকাডিলি সার্কাসে পৌঁছেই একটা কান্ড হল। এক বয়স্ক শ্বেতাঙ্গ দম্পতি হঠাই নার্ভাস আমাকে ধরে কেয়ারিনক্রসে কী করে যাবেন তা জিজ্ঞেস করলেন। ছাত্রাবস্থায় কেয়ারিনক্রসের ইকনমিক্সের বই পড়েছিলাম। সেই লেখকের সঙ্গে এ জায়গার সম্পর্ক আছে কি না বুঝলাম না?
অত্যন্ত বিজ্ঞের মতো তাদের সমঝিয়ে-টমঝিয়ে দিলাম।
ভদ্রলোক বিস্তর থ্যাঙ্ক-উ ট্যাঙ্ক-উ বলার পর ভোলা চশমার ফাঁক দিয়ে চোখ তুলে শুধোলেন, হোয়ার উ ফ্রম?
পরবর্তী দিনগুলোতে এ প্রশ্ন বহুবার শুনতে হয়েছে।
কিন্তু প্রথমবার অবাক লাগল।
বললাম, ইণ্ডিয়া।
ভদ্রলোক বললেন, আমি তাই অনুমান করেছিলাম।
আমি বললাম, মশায়ের নিবাস?
ভদ্রলোক বললেন, আয়ারল্যাণ্ড। আমার বয়েস বাহাত্তর। সারাজীবন কাজ-কর্ম করে সস্ত্রীক এই প্রথম লানডানে এলাম। শহর দেখতে।
সেকথা শুনে বররমপুরের লোকের মতো আমার আবারও বলতে ইচ্ছে হল, বলেন কী গো আপনি?
কিন্তু বলা হল না।
নিজেকে খুব খুশি খুশি লাগল। আমি এই বয়েসেই যদি কলকাতা থেকে লানডান দেখতে এসে থাকতে পারি তাহলে এই বাহাত্ত্বরে আইরিশ বুড়ো-বুড়ির চেয়ে আমি যে বেশি ভাগ্যবান সে বিষয়ে সন্দেহ কী?
লানডানে টুরিস্টরা এসেই যা-কিছুকে প্রধান করণীয় কর্তব্য বলে মনে করে আমি তার কিছুই করলাম না। কারণ, আমার ভালো লাগে না। সবাই যা করে তা করতে আমার কখনোই ভালো লাগেনি।
রানির বাড়ির গার্ড বদল দেখতে গেলাম না, মাদাম তুসোর মোমের গ্যালারি দেখতে গেলাম না, বাকিংহাম প্যালেস, দশনম্বর ডাউনিং স্ট্রিট এমনকি শার্লক হোমসের বাড়ি পর্যন্ত না। কিছুই না করে পিকাডিলি সার্কাসের পথে পথে ঘুরে বেড়িয়ে এক ফিরিওয়ালার, যে একটা বন্ধ দোকানের শো-কেসের রকে বসে জাম্পিং-বিনস বিক্রি করছিল, পাশে থেবড়ে বসে পড়ে তার সঙ্গে গল্প জমালাম।
মানুষ সে যে-দেশের মানুষই হোক না কেন আমাকে যত আকৃষ্ট করে, তাদের সঙ্গে যত সহজে একাত্মতা বোধ করি; তেমন কোনো বাড়িঘর স্মৃতিসৌধ কিছুর সঙ্গেই কখনো করিনি। ইতিহাসের প্রতি আমার অবজ্ঞা নেই–কিন্তু অতীত-ইতিহাসের চেয়ে বর্তমানের একজন সাধারণ অজ্ঞাতকুলশীল মানুষ আমাকে অনেক বেশি আকর্ষণ করে। মানুষের চেয়ে বেশি ইন্টারেস্টিং মনুমেন্ট অথবা জীব-জন্তু আমার আজও চোখে পড়েনি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন কাটিয়ে দিতে পারি আমি অচেনা অজানা মানুষদের মধ্যে। তারা যত সহজে আমাকে আপন করে নিতে পারে অথবা আমি তাদের; সেটা খুবই স্বাভাবিক বলে মনে হয়।
সকলে বলেন যে, ইংরেজ জাতটা খুব রিজার্ভড়। কেউ পরিচয় না করিয়ে দিলে তারা কারও সঙ্গেই পরিচিত হতে চায় না। আমার সামান্য অভিজ্ঞতায় মনে হয়েছে যে কথাটা সর্বৈব ভুল। ওদের দম্ভ ও গাম্ভীর্যটা পুরোপুরি বাইরের মুখোশ। আমার মতটা নির্ভুল না-ও হতে পারে।
এ বিষয়ে ঠাণ্ডা মাথায় অনেক ভেবে-টেবে এই সিদ্ধান্তেই শেষপর্যন্ত উপনীত হওয়া গেল যে পৃথিবীর তাবৎ স্ত্রী-পুরুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একইরকম। রঙের কিছু হের-ফের আছে। সে নিছকই প্রাকৃতিক কারণে। যে-কারণে সুন্দরবনের বাঘের রং আর হাজারিবাগের বাঘের গায়ের রঙের তারতম্য ঘটে সেই একই কারণে মানুষদের গায়ের রং-তারতম্য ঘটে। তা ছাড়া মস্তিষ্কের কোষের মধ্যে ধূসর-রঙা যে পদার্থটি ব্ৰহ্মসাহেব মগজে ইনজেকশান দিয়ে প্রত্যেক মানুষকে পৃথিবীতে পাঠান তাতে সাহেব ও বাঙালির মধ্যে কোনোরকম তারতম্য রাখেন না। পৃথিবীর সব দেশের সব মানুষের বেসিক ইমোশান একইরকম। সে কারণে আফ্রিকান ওকাপীর পক্ষে, সাউথ আমেরিকার বাঁদরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা জমানো যতখানি কঠিন তার তুলনায় আমার পক্ষে একজন অপরিচিত ইংরেজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা জমানো ঢের সহজ।
তবে সায়েবগুলো ছোটোবেলা থেকে যাত্রাটা ভালো করতে শেখে। ওদের বুদ্ধিসুদ্ধি সব বোগাস। ওরা বেনের জাত বটে কিন্তু কলকাতার বড়োবাজারের যে-কোনো মাড়োয়ারি ব্যাবসাদার বা নদিয়া জেলার পলাশিতে শিকড় গেড়ে বসা পূর্ববঙ্গের যে-কোনো সাহাবাবু এদের কানে ধরে বেনে-বুদ্ধি শিখিয়ে দিতে পারে।
সত্যি কথা বলতে কী এদের খুব কাছ থেকে দেখার পর আমার বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় যে কি করে এরা আমাদের ওপর এতদিন প্রভুত্ব করে গেল!
মনে হয় প্রভুত্ব করাতে তাদের যতটুকু বাহাদুরি ছিল, দাসত্ব স্বীকারে আমাদের বাহাদুরি তার চেয়ে প্রবলতর ছিল। আমার পরিচিত এক ভদ্রলোক আছেন যাঁর ধমনিতে মাতৃকুল পিতৃকুলের জমিদারি নীল রক্ত বাহিত হচ্ছে বলে সকলে জানে। একদিন আমারই সামনে তাঁর বুড়ো আঙুলে পিন ফুটে যাওয়ায় রক্তপাত ঘটে। বিশেষভাবে লক্ষ করার পরও তাঁর রক্তের সঙ্গে কচ্ছপের রক্তের রঙের কোনো পার্থক্য আমার নজরে আসেনি।
তিনি এক সাহেবি কোম্পানিতে কাজ করেন। সাহেবরা পান খাওয়া অপছন্দ করেন বলেই তিনি দেশ স্বাধীন হওয়ার এত বছর পরও পান খান না। সেই কারণেই তাঁর অফিসে আমার যখনই যেতে হয় আমি ধর্মীয়ভাবে চারখিলি পান মুখে পুরে তাঁর কাছে যাই। তাঁর বাড়ির বারান্দায় এখনও ইংল্যাণ্ডেশ্বর ষষ্ঠ জর্জের গুফো ছবি টাঙানো আছে এবং তাঁর অন্নপ্রাশনের সময়ে বাংলার লাটসাহেব এসে যখন তাঁর ঊর্ধ্বতন চোদ্দপুরুষকে উদ্ধার করেছিলেন তখনকার সেই অনুষ্ঠানের ছবিও জ্বলজ্বল করছে। লাটসাহেব সেদিন না এলে সেই চোদ্দপুরুষের যে কী গতি হত তা ভাবলে মাঝে মাঝে শিহরিত হয়ে উঠি আমি।
এই সব দুষ্প্রাপ্য কিছু কিছু নিদর্শন কলকাতার নামকরা ক্লাবে মাঝে মাঝে দেখতে পাই। ভারতীয় গণ্ডার দুষ্প্রাপ্য হয়ে যাচ্ছে এ যেমন দুঃখের খবর এই সব ক্ষণজন্মা পুরুষও যে শনৈঃ শনৈ: এদেশে দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠছেন এটা একটা সুখের খবর যে তাতে কোনোই সন্দেহ নেই।
স্বীকার করতে লজ্জা নেই যে, বাংলাদেশে নেতাজি, বিধান রায়, বিনয়-বাদল-দীনেশ ক্ষুদিরাম, বীণা দাস যেমন ছিলেন তেমন এরকম পা-চাটা লোকেরও কখনো অভাব ঘটেনি। তাঁদের চরিত্রের প্রধান গুণ পদলেহন। এখন শ্বেতাঙ্গদের পা চাটতে পাচ্ছেন না সেই দুঃখ অন্যান্য অনেক পা চেটে পুষিয়ে নিচ্ছেন তাঁরা। যেদিন এই সব পদলেহনকারীদের মুখে জুতোসুদ্ধ লাথি মারার লোক জন্মাবে সেদিন এ দেশের বড়োই সুদিন আসবে।
অস্ট্রিয়ান এমব্যাসি খুঁজে বের করে ভিসা নেব এই অভিপ্রায়ে বেরিয়ে বাঁই বাঁই করে চক্কর খাচ্ছিলাম। এদেশে আমাদের দেশের মতো ভ্যাগাবণ্ড ভলান্টিয়ার নেই যে আকছার বিনি পয়সায় পথ-বাতলানোর লোক পাবেন।
একজন মহিলাকে সামনে পেয়ে পথ শুধোলাম। মহিলা সুন্দরী। আমারই সমবয়েসি। আমার প্রশ্ন শুনে থমকে দাঁড়ালেন। হাসলেন একটু। তারপর বললেন, একসেকেণ্ড দাঁড়ান। বলেই হাতব্যাগের মধ্যে থেকে লানডানের রোড ম্যাপ বের করে আমাকে পথ বাতলে দিলেন।
আমি ধন্যবাদ দেওয়ার আগেই উনি আবারো মিষ্টি হাসলেন। তারপর মেয়েলি লজ্জান গলায় বললেন, আমিও ট্যুরিস্ট। আমি অস্ট্রেলিয়া থেকে এসেছি কাল।
লজ্জায় আমার মাথা কাটা গেল।
আসলে আমরা ছোটোখাটো ব্যাপারেও বড়ো অলস, পরর্নিভর। এটা আমাদের ভারতীয় চরিত্রের একটা বড়ো দোষ। যখন ওরা কোনো ব্যাপারেই কারও ওপরে নির্ভরশীল হওয়াকে লজ্জাকর বলে মনে করে আমরা আমাদের সব দায়িত্ব এমনকী পথচলার ও পথখোঁজার দায়িত্বটুকুও অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে শুধু নিশ্চিন্ত নই; আশ্বস্ত বোধ করি।
দূর থেকে দেখলাম একজন পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে। লানডানের পুলিশের নাম শুনেছি অনেক। এগিয়ে গিয়ে দেখি সাড়ে ছ-ফিট চেহারার মলাটে একটি বালখিল্য। ভালো করে দাড়ি-গোঁফ ওঠেনি। মাকুন্দও হতে পারে।
সাহেবরাও কি মাকুন্দ হয়? কে বলতে পারবে? জানি না। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা দেখলে হয়।
ছেলেটিকে গিয়ে পথ শুধোতেই সে তার সাড়ে ছ-ফিট জিরাফের মতো ঘাড় আমার পাঁচ সাড়ে-দশ মুখের কাছে নামিয়ে এনে মেলায়েম গলায় বলল, ইয়েস স্যার? হোয়াট ক্যান আই ডু ফর ইউ স্যার?
শুনে সুড়সুড়িতে মরে গেলাম। সায়েবরা স্যার স্যার করলে কী যে সুড়সুড়ি লাগে, কী বলব!
তাকে বললাম, আমার জিজ্ঞাসার কথা।
সে অত্যন্ত সপ্রতিভতার সঙ্গে বলল, সার্টেনলি স্যার। আই উইল শো ইউ দ্য ওয়ে স্যার। বলেই আমার কেনা গোলামের মতো আমার সঙ্গে সঙ্গে এক ফার্লং হেঁটে গিয়ে অস্ট্রিয়ান এমব্যাসি দেখিয়ে দিল। দিয়ে বলল, হিয়ার ইউ আর স্যার!
আমি বললাম, দেখো বাপু তোমাদের কথা ছোটোবেলা থেকে শুনে আসছি। আজ দেখে চক্ষু কর্ণ সার্থক হল। তোমার সোনার বেটন হোক, লাল টুকটুকে বউ হোক।
মনে মনে আরও অনেক কিছু বললাম, ছেলেটি শুনতে পেল না। কিন্তু সত্যিই বড়ো ভালো লাগল। পাবলিক সার্ভেন্ট এদেরই বলে; পাবলিক এদের সার্ভেন্ট নয়, এরা সত্যিই পাবলিকের সার্ভেন্ট।
পৃথিবীতে একমাত্র লানডানেই পুলিশের কাছে কোনো অস্ত্র থাকে না। অস্ত্রের মধ্যে একটা ছোটো বেটন আর বাঁশি। অন্যান্য সব দেশের পুলিশের কাছে রিভলবার বা পিস্তল থাকে। কখনো একাধিকও।
আইন ও শৃঙ্খলার প্রতি দেশের প্রতিটি লোকের কতখানি সম্মান থাকলে খালি হাতে লানডানের পুলিশ ঘুরে বেড়াতে পারে রাত্রি-দিন তা সহজেই অনুমেয়।
ইংল্যাণ্ডে আসার আগে টবী বহুদিন জার্মানিতে ছিল। ওর সেই প্রথম দিককার কষ্টের দিনগুলোরকথা শুনলে সত্যিই চোখে জল আসে।
ইন্টারমিডিয়েট পাস করে কী করবে মনস্থির করতে না পেরে ওর কয়েকজন অদূরবর্তী ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বন্ধুদের সঙ্গে ও পশ্চিম জার্মানিতে পাড়ি দিয়েছিল।
বাঙালির স্কুলে পড়েছে, ফ্রেঞ্চ, ল্যাটিন দূরে থাক, ইংরেজিটা পর্যন্ত তেমন বলতে পারে না তখন। লিখতে পারে মোটামুটি।
তখনকার দিনে কলকাতার হগবাজারে একরকম বাঙালি দোকানি দেখতে পাওয়া যেত। এখন সিন্ধী দোকানদারের ভিড়ে তারা প্রায় হারিয়ে গেছে, হারিয়ে গেছে তাদের খদ্দেররাও। তাদের প্রত্যেকেই প্রায় কাজ-চালানো ইংরেজি বলতেন-টেক তো টেক, নো টেক নো টেক, একবার তো সি গোছের।
টবীর এবং শুধু টবীর কেন, অনেক বাঙালি পন্ডিত ইংরেজির অধ্যাপকদের কথ্য ইংরেজিও তখন তদনুরূপ ছিল। আজকের ভারতবর্ষে, তথা বাংলাদেশে কথ্য ইংরেজির মান অনেক উঁচু হয়েছে। এর কারণ ইংরেজ-প্রীতি যতটা নয়, ততটা স্বাধীনতোত্তর যুগে এক প্রদেশীয় শিক্ষিত লোকেরা অন্য প্রদেশীয় লোকেদের অনেক কাছাকাছি আসাতে ইংরেজি ভাষাটার অনেক বেশি চল হয়েছে। কথ্য ভাষা হিসেবে।
যাই-ই হোক, এইরকম ইংরেজির এবং কোনোরকম জার্মান ভাষার জ্ঞান ব্যতিরেকেই টবী এক শীতের দিনে জাহাজ থেকে নেমেছিল পশ্চিম জার্মানিতে।
ভাবলেও, দুটো হাত ওভারকোটের পকেটে ঢোকাতে ইচ্ছে করে আমার।
প্রথম চাকরি টেলিগ্রাফের তারে জমে থাকা বরফের স্কুপে সাত-সকালে মইয়ে চড়ে উঠে নুন ছিটানো। বরফ গলাবার চাকরি। জার্মানির শীতের সম্বল চাঁদনিতে কেনা একটি কম্বলের গরম কোট।
সেইসব দিনের কথা বলতেও টবীর চোখ জ্বলজ্বল করে–আমার শুনতে চোখ ছলছল করে।
যাই-ই হোক, সেই টবী, জীবন আরম্ভের টবী। আজকের টবীকে দেখে সেই টবীর কথা ভাবা যায় না।
পাশ্চাত্যের এই জিনিসটা আমাকে বড়ো মুগ্ধ করে। আমাদের দেশে রাজার ছেলে প্রায়শই রাজা হয়, মন্ত্রীর ছেলে মন্ত্রী, মসৃণভাবে না হলে এই ঘটনা অমসৃণভাবে ঘটানো হয়। এবং চাষার ছেলে চাষা। পাশ্চাত্যের মতো উত্থান-পতন, ডিগবাজি-অভ্যুত্থান আমাদের দেশে এখনও তেমন আকছার নয়। তাই-ই হয়তো ওদের জীবন এত ইন্টাররেস্টিং, ওরা জীবনকে এত ভালোবাসে; এত সম্মান করে।
সেদিন অফিস থেকে ফিরেই টবী বলল, রুদ্রদা, আজ আমরা একটা অস্ট্রিয়ান রেস্তোরাঁয় খেতে যাব অস্ট্রিয়ান ভিসা যখন হলই।
আমি বললাম, যথা আজ্ঞা।
স্মিতা সাজুগুজু করতে করতে টবী বসার ঘরের বুকশেলফের মধ্যবর্তী ছোট্ট সেলার খুলে টকাটক দুটো নিট লাল-রঙা স্কটল্যাণ্ডের জল মেরে দিল।
দাদাকেও প্রণামী দিল।
বাইরে বৃষ্টি হচ্ছিল। দাদা বিশেষ গাঁই-ছুঁই না করে ছোটোবেলায় মায়ের হাত থেকে নিয়ে যেমন বিনা প্রতিবাদে ক্যাস্টর অয়েল খেত, তেমনি বিনা আপত্তিতে হুইস্কি খেল। একটু খুশিও হল খেয়ে।
স্মিতার হয়ে গেলে সকলে মিলে নীচে এসে, গাড়িতে ওঠা গেল।
লানডানের বেজওয়াটার পাড়াটা খুব রমরমে পাড়া। একেই বলে, এককথায় বেড-সিটার পাড়া। অর্থাৎ, এক-কামরার সব ঘর ভাড়া পাওয়া যায় এখানে। বেডরুম-কাম-সিটিং-রুম– এককথায় : বেড-সিটার।
এ পাড়ার বাসিন্দা বেশির ভাগই মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত ছাত্রছাত্রী, বকা-বাউণ্ডুলে, হিপি হিপিনি। সারারাত এ পাড়ায় দোকানপাট খোলা। সোহোর মতো, নিউইয়র্কের ব্রডওয়ের মতো, প্যারিসের মতো; এখানে রাতে-দিনে বিশেষ তফাত নেই। এইসব বেড-সিটার ঘরে থেকেই বহু ছেলেমেয়ে থিসিস সাবমিট করে ডক্টরেট হচ্ছে, অনেকে বেবাক বকে যাচ্ছে, কেউবা হাসিস, মারিজুয়ানা, এল এস ডি খেয়ে ঝুঁদ হয়ে রয়েছে, কেউ বা গর্ভবতী হচ্ছে, কেউ গর্ভপাত ঘটাচ্ছে। মোট কথা, এমন তালেবর স্বাধীন স্বর্গ-নরক জায়গা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে খুব কমই আছে।
টবীর গাড়িটা এসে ওয়েস্টবোর্ন রোডে দাঁড়াল।
গাড়ি পার্ক করে আমাদের নিয়ে টবী রেস্তোরাঁ নামক যে অতিসন্দেহজনক গর্তটার সামনে দাঁড় করাল, তাতে প্রথমে মনে হল যে ভাই আমার গরিব দাদাকে কলকাতার কোনো ক্লাস থ্রি, গ্রেড থ্রি স্ট্যাণ্ডার্ডের রেস্তোরাঁয় এনে ডিমের ডেভিল বা ভেজিটেবল চপ-টপ কিছু খাইয়ে সস্তায় সারবে বলে মনস্থ করেছে।
সেই সুড়ঙ্গ বেয়ে গর্তে ঢোকা পর্যন্ত খারাপ লাগলেও ভেতরে পৌঁছে একেবারে জমে গেলাম।
জমে গেলাম না বলে, সেঁটে গেলাম বলা ভালো।
ভাই সব, যদি ও তল্লাটে ধাওয়া-টাওয়া হয়ে ওঠে কখনো, তাহলে এই গর্তে একবার ঢুকতে ভুলবেন না। এই ছোটো অস্ট্রিয়ান রেস্তোরাঁর নাম Tyroller Hut : ২৭ নম্বর ওয়েস্টবোর্ন রোড, বেজওয়াটার, ডবলু : ২, লানডান। সোমবার বন্ধ থাকে। মঙ্গলবার থেকে রবিবার অবধি খোলা।
আমি কমিশন পাই না।
অস্ট্রিয়ার মতো জায়গা এবং অস্ট্রিয়ান লোকেদের মতো লোক হয় না। Tyrol-অস্ট্রিয়ার ছবিসদৃশ ইনসব্রুক প্রভিন্স-এর একটি জায়গা। Tyrol-এ যাবার সুযোগ ঘটেছিল এই লেখকের। সেকথা পরে কোনো সময়ে বলা যাবে।
সেই গর্তে ঢুকতেই দেখি গুচ্ছের জার্মান ও অস্ট্রিয়ান নারী-পুরুষ ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে কনুইতে কনুই ঠেকিয়ে বসে খানাপিনা করছে।
জার্মান ভাষায় ইংরেজি Hut (উচ্চারণ হাট) কে হুট বলে। আমাদের বাংলায় হুট করে এল বা হুট করে চলে এলর সঙ্গে এই হুটের কেমন একটা প্রকৃতিগত মিল খুঁজে পেলাম।
কাঠের তৈরি লগকেবিন যেমন হয় রেস্তোরাঁর ভেতরটাও তেমনি। অ্যাকর্ডিয়ান ও গোরুর গলার ঘণ্টা বাজিয়ে টরলের লোকেরা নানারকম গান গায়। একজন লোক সঙ্গী-সাথিদের নিয়ে কাউবেল বাজিয়ে ও অ্যাকর্ডিয়ান ঝাঁকিয়ে জব্বর গান ধরেছেন। তাঁর সঙ্গে গলা মিলিয়েছেন প্রায় সব খদ্দেররা। বেশির ভাগই প্রৌঢ়। বিপুল-বিপুলা।
এদের এত প্রাণ, এত ফুর্তি, এত আনন্দের ফোয়ারা, এত হাসি কোত্থেকে আসে তা ভাবলেও অবাক লাগে।
আমার বারেবারেই মনে হয়েছে যে, এই আনন্দ শুধুমাত্র আর্থিক সচ্ছলতা থেকেই আসতে পারে না। ওদের মধ্যে আরও যেন কী আছে। হয়তো চিন্তা-ভাবনাহীনতা, হয়তো দেশ ও সমাজ ওদের বেশির ভাগ দায়িত্ব থেকেই মুক্ত করেছে, এবং ওরাও দেশকে মুক্ত করেছে বলে। দেশ থেকে সাধারণ বিযুক্ত নয় বলেই বুঝি ওরা এমন করে হাসতে পারে, গাইতে পারে; বাঁচতে পারে।
অন্যভাবে দেখতে গেলে বলতে হয় এবং ওদের ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনে যা-কিছুই পেয়েছে তার জন্যে বুঝি অনেক মূল্য দিয়েছে। একদিন অনেক চোখের জল, বুকের রক্ত ঝরিয়েছে; তাই আজকের হাসি ওদের এমন দ্বিধাহনি সাবলীল।
ভালো করে জমিয়ে বসে, টবী প্রথমে Lager Beer-এর অর্ডার করল।
বলল, এটা স্টার্টার।
আমি বললাম, এটা কি ফোর-ফর্টি রেস নাকি? কী সব স্টার্টার-ফার্টার বলছিস, মানে বুঝছি না।
টবী বলল, দেখোই না তুমি।
ইউনিয়ন জার্মান Lager Beer-এর সঙ্গে কী যেন খাদ্যও একটা অর্ডার দিল। বলল, সেটাও নাকি স্টার্টার।
আমি ভাবলাম, এবার পিস্তলের আওয়াজ-টাওয়াজ শুনতে পাব।
কিন্তু কিছুই না হয়ে, একটি সুন্দরী অস্ট্রিয়ান মেয়ে পেঁপের মতো দেখতে কিন্তু দারুণ স্বাদ ও পেঁপের চেয়ে শক্ত মধ্যিখান দিয়ে চেরা একটি ফলের মধ্যে Prawn Cocktail দিয়ে গেল। তার বাইরে বাঁধাকপির পাতা।
টবীকে ভয়ে ভয়ে শুধালাম, এটারে কী কয়?
স্মিতা হেসে উঠল।
বলল, এই শুরু করলে রুদ্রদা।
টবী গম্ভীর মুখে জার্মান উচ্চারণে বলল, Avacadomit Garmeen।
প্রথমে ভাবলাম, জার্মান ভাষায় আমাকে গালাগালি করল বুঝি।
কিন্তু না, পরক্ষণেই রীতিমতো মেনুকার্ড খুলে দেখাল নামটা।
যে ছেলেটি অ্যাকরডিয়ান বাজাচ্ছিল তার কাছাকাছিই ভিড় বেশি। যাঁরাই খেতে এসেছিলেন তাঁরাই প্রায় এই গানে গলা দিচ্ছিলেন।
জার্মান ভাষা ও রাশিয়ান লোকদের চেহারা আমার মোটেই পছন্দ হয় না। কিন্তু এই প্রথম জার্মান ভাষার গান বাজনা শুনে প্রত্যয় হল যে গান গাইলে মিষ্টিই লাগে।
টবী জার্মানদের মতোই জার্মান বলে। এখানে এসে পড়ে ও ওর মন্ত্রমুগ্ধা স্ত্রী ও ক্যাবলা দাদাকে ওর জার্মান ভাষায় স্তম্ভিত করে রাখল। যে-দুজন ওর টেবিলে বসে ছিল (অর্থাৎ আমরা দুজন) তাদের কেউই জার্মানের জও জানি না, অতএব ও আদৌ জার্মান ভাষায় কথা বলছিল কি না তাও ধরার উপায় ছিল না।
ইতিমধ্যে Steinhager Schnapps দু-ঢোক খেয়ে অবস্থা কাহিল। এই সাদাটে তরলিমা কবে আবিষ্কৃত হয়েছে জানি না, তবে সময়মতো এর গুণাবলি সম্বন্ধে অবহিত হলে হিটলার সাহেব ফ্লাইং-বম্বস না পাঠিয়ে এই দিয়েই ইংল্যাণ্ড ধ্বংস করতে পারতেন।
টবী বলল, এ একরকমের লিকার ব্র্যাণ্ডি। টিপিক্যালি জার্মান।
কথাবার্তা বলতে বলতে খেতে খেতে হঠাৎ এক বিপত্তির সৃষ্টি হল। আমার পাশের টেবিলে-বসা এক বর্ষীয়সী, স্থূলাঙ্গী কিন্তু ভারি হাসিখুশি মিষ্টি জার্মান মহিলা আমার এক হাত সজোরে আকর্ষণ করলেন।
বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখি গানের সঙ্গে সঙ্গে ওই ছোটো রেস্তোরাঁর প্রত্যেকে হাতে হাত রেখে গান গাইছেন এবং একবার উঠে দাঁড়াচ্ছেন আর একবার বসছেন। আপস অ্যাণ্ড ডাউনস বলতে বলতে।
ভর-সন্ধেবেলায় খেতে খেতে এমন ডন-বৈঠকি মারার তাৎপর্য না বুঝলেও এটুকু বুঝতে অসুবিধা হল না যে ও-জাতটার মধ্যে প্রাণপ্রাচুর্য বড়ো বেশি। এদের যা-ইচ্ছে-তাই না করতে দিলে এরা আবার কবে কার সঙ্গে যুদ্ধ লাগিয়ে দেবে তার ঠিক নেই। জার্মানদের মতো এমন দিল-খোলা হাসিও বুঝি ইউরোপের আর কোনো দেশের লোক জানে না। ওদের হৃদয়ের কাছে যত সহজে পৌঁছোনো যায় তত সহজে বোধহয় খুব কম দেশের লোকের কাছেই।
কিছুক্ষণ ধ্বস্তাধ্বস্তি করতে হলেও হাত ধরাধরি করে ওদের সঙ্গে, ভারি ভালো লাগল ওদের এই সপ্রাণ গান-বাজনা, এই হাসি, অপরিচিত বিদেশিকে বিনাদ্বিধায় মুহূর্তের মধ্যে নিজেদের একজন করে নেওয়ার ক্ষমতা দেখে।
হঠাৎ চোখ পড়ল, আমাদের সামনেই এক টেবিলে একটি মেয়ের দিকে। তার বয়েস বেশি না। আমার সঙ্গে স্বচ্ছন্দে বিয়ে হতে পারত। কিন্তু হয়নি। ভাবও হতে পারত। কিন্তু তাও হয়নি।
তাহলে কেন হয়নি বলি।
মেয়েটি একটা কালো কার্ডিগান পরেছিল। ভারি সুন্দর চাঁপা-রঙা ডান হাতে সোনালি রিস্টওয়াচ। বাঁ-হাতে একটা বালা। এমন সুন্দর ও বুদ্ধিভরা মুখ বড়ো একটা দেখা যায় না। তার চোখের দিকে চাইলে মনে হয় কোনো অভ্রখনির অতলে তলিয়ে যাচ্ছি, আর কখনো উঠতে পারব না বুঝি।
তার দিকে অপলকে চেয়ে থাকতেই টবী বলল, কী গো রুদ্রদা, ভালো লেগেছে তো গিয়ে আলাপ করো। তোমার দিকেও বার-বার চাইছে মেয়েটি। আজ শুক্রবারের সন্ধেবেলা আজকেই তো বন্ধুত্ব করার সময়।
আমি চুপ করে রইলাম।
Schnapps ও এই মেয়েটির চোখে, আমার নেশা ধরে গেছিল।
আমি আবারও ওদিকে চাইতে টবী বলল, খী খারবার।
তার পরেই বলল, এ কি আমাদের দেশ পেয়েছ না কি? চোখে চোখে কথা কও মুখে কেন কও না? ওসব আমাদের দেশের জিনিস। এই স্পিডের দুনিয়ায় কারোই চোখের শোনার মতো সময় ও সময় থাকলেও নির্ভুলভাবে বোঝার এলেম নেই। মুখে না বললে এখানে কোনো কিছুই ঘটবে না। এবং নিজ মুখেই বলতে হবে। বন্ধু-বান্ধব, বোন, বউদি এখানে সব বেকার। বাঙালিরা প্রেম করার ব্যাপারেও পরের সাহায্যের ওপর ভরসা করে বসে থাকে–বাঙালির কি কিসসু হবে? তুমিই এল?
আমি বললাম, এই মুহূর্তে আমি রামমোহন রায় বা বিবেকানন্দ হতে চেয়ে তাবৎ বাঙালির ভাগ্য-নির্ধারণ করতে চাই না, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমার যে কিছুই হবে না তা মর্মে মর্মে বুঝতে পারছি।
স্মিতা বলল, অত নিরাশ হবার কী আছে? তোমার প্রতি ভীষণ ইন্টারস্টেড মনে হচ্ছে মেয়েটি। বান্ধবীর সঙ্গে কথা বলছে কিন্তু চেয়ে আছে তোমার দিকে।
বুঝলাম। আমি বললাম।
তারপর বললাম, ঢাকাই কুট্টিদের একটা গল্প চালু ছিল ছোটোবেলায়।
কী গল্প?
ঢাকাই কুট্টি দাঁড়িয়ে আছে অন্যদের সঙ্গে ঘোড়ার-গাড়ির গায়ে হেলান দিয়ে–এমন সময়ে অতীব সুন্দরী হিন্দুর মেয়ে চলে গেল পাশ দিয়ে।
কুট্টি অনেক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে থাকল।
কিছু করল না বা বলল না? অবাক হয়ে স্মিতা শুধোল।
না। আমি বললাম।
তখন কিছুই বলল না। কিন্তু সম্পূর্ণ চোখের আড়াল হলে বলল, এহনে গ্যালা, হাঁইটা গ্যালা গিয়া হুন্দরী; যাও। কিন্তু হপ্নে?
মানে? স্মিতা ও টবী একইসঙ্গে শুধোল।
মানে? এখন তো চলে গেলে সুন্দরী, হেঁটে হেঁটে চলে গেলে।
–এখন গেলে, তো যাও। কিন্তু স্বপ্নে? স্বপ্নে যাবে কোথায়?
খী-খারবার, বলে টবী চেঁচিয়ে উঠল।
স্মিতা শীতের সকালের হাসির মতো শী-শী করতে লাগল।
চারপাশের জার্মানরা গান থামিয়ে চেয়ে রইল আমাদের দিকে।
কিন্তু আমি চোখ তুলে দেখলাম, সেই সুন্দরীর বয়-ফ্রেণ্ড এসে গেছে।
স্বপ্নই সার। বাঙালির স্বপ্নই সার।
ইতিমধ্যে টবী যা খাওয়ার অর্ডার দিয়েছিল, তা এসে হাজির। মেইন-ডিশ।
তিনজনে তিনরকম খাবার অর্ডার দিয়েছিলাম–জার্মান মেনুকার্ড দেখে। বলাবাহুল্য আমি অচেনা ঘোড়ার নাম দেখে, তাদের চেহারা না-দেখেই রেসের টিকিট কাটার মতো মেনুকার্ডে তর্জনী ছুঁইয়েছিলাম। খাবার না এসে স্বচ্ছন্দে ফিঙ্গার-বোল অথবা টুথপিকও আসতে পারত।
কিন্তু খাবার যখন এল, তখন রীতিমতো উত্তেজনার কারণ ঘটল।
আমাকে দিয়েছিল, Eisbeinmit Saurkaraut.
নাম শুনে বাঙাল আমি ঘাবড়েছিলাম বলে, পাঠকের ঘাবড়াবার কোনোই কারণ দেখি না। ব্যাপারটা হচ্ছে শুয়োরের নরম পা–টক টক বাঁধাকপির সঙ্গে সার্ভ করেছে। খেতে জব্বর।
স্মিতা নিয়েছিল Paprikahuhn Nact Ungarisher Art Mit Rice.
ব্যাপারটাকে পাঁপড় অথবা পাপড়ি ইত্যাদি বলে ভুল করবেন না। জার্মান নামের ওরকমই ছিরি! অর্থাৎ, হাঙ্গারিয়ান প্রথায় রান্না চিলি-চিকেন ভাতের সঙ্গে সার্ভ করেছে।
আর টবী নিয়েছিল Rinds Roulade Mit Nudlen-অর্থাৎ স্টাফড বিফ, সঙ্গে ব্যাকন; শশা আর সর্ষে।
এ তো গেল খাদ্য। মেইন ডিশের সঙ্গে খাওয়ার জন্যে পানীয়ও এল। রেডওয়াইন। নাম তার ষাঁড়ের রক্ত। বুলস ব্লাড়। তা পান করে শরীরে ষাঁড়ের বল বোধ করতে লাগলাম প্রায়। তার সঙ্গে মাঝে মাঝেই জার্মান স্ন্যাপস।
স্ন্যাপস জিনিসটা সত্যিই অতিসাংঘাতিক। এমনি গ্লাসে ঢেলে রাখলে দেখে মনে হবে রিফাইনড ক্যাস্টর অয়েল, কিন্তু খেলে মস্তিষ্কর কোষে কোষে কে রে-কে রে রব উঠবে।
যাই-ই হোক, ভায়ার ঘাড়ে ভালো করে খাদ্য-পানীয় সব কিছু রীতিমতো রেলিশ করে খাওয়া গেল।
যখন টিয়োলার হুট থেকে বেরুলাম তখন অনেক রাত। কিন্তু বেজওয়াটারে রাত চিরদিনই সব প্রহরেই সন্ধে থাকে। সায়েবরা বলে, নাইট ইজ ভেরি ইয়াং। কথাটা এখানে সর্ব সময়েই খাটে।
কতরকম স্পোর্টস-কার যে দাঁড়িয়ে আছে পথের দু-পাশে তা বলার নয়। যেমন গাড়ির চেহারা, তেমনই সুন্দর যাত্রীদের চেহারা। অর্থ, বিত্ত, স্বাধীনতা এবং নিজ-নিজ জীবনকে প্রতিমুহূর্তে নিংড়ে নিংড়ে উপভোগ করার অসীম আগ্রহ এদের এমনভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছে যে, চোখ মেলে দেখলে ঈর্ষা হয়।
ভাবতে ভালো লাগে যে, একদিন আমাদের এমন সুন্দর ভারতবর্ষের লোকেরাও এমনি করে ভালোবাসতে শিখবে জীবনকে, জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে। চিনে নেবে নিজের দেশকে। অন্তরের গভীরে জেনে গর্বিত হবে যে, এমন দেশ পৃথিবীতে আর দুটি নেই–শুধু নিজেদের প্রত্যেককে যোগ্য করে তুলতে হবে, এই দেশ নিয়ে দেশের ও দেশের লোকেদের সত্যিকারের ভালোর জন্যে কী করণীয় এবং অকরণীয়, তা একদিন প্রাঞ্জলভাবে সকলেই বুঝবে।
বুঝবে কি?
দেখতে দেখতে আমরা অপেক্ষাকৃত ফাঁকা রাস্তায় এসে পড়লাম। জোরে গাড়ি চলেছে মিডেকসের দিকে। হলদে স্বপ্নের মতো দেখাচ্ছে পথ-ঘাট মার্কারি ভেপার ল্যাম্পের আলোয়।
স্ন্যাপস-এর নেশা কেটে গিয়ে হঠাৎ-ই আমাকে এক হীনমন্যতা, অপারগতার বোধ রাতের কুয়াশার মতো ঘিরে ফেলল। আমার মনে হল, ভারতবর্ষ বলতে যা বোঝায় সেই কোটি কোটি সরল, সাদা স্বল্লবিত্ত, গ্রাম ও বন-পর্বতবাসীদের সম্বন্ধে আমরা কতটুকুই বা জানি, বুঝি বা বোঝবার চেষ্টা করি? আমরা এ ভারতবর্ষের ক-জন? তারাই তো সব। কিন্তু তাদের কি আমরা ভালোবেসেছি, জেনেছি যেমন করে জানার তেমন করে? কিছু কিছু লেখক তাঁদের নিয়ে লিখেছেন, কিন্তু বাংলা সাহিত্যে এমন ক-জন বলিষ্ঠ দরদি সাহিত্যিক আছেন যাঁরা নিজের চোখের দৃষ্টি এবং কল্পনা মিলিয়ে দেশের সাধারণ লোকদের কথা লিখেছেন, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও কষ্টের স্বরূপকে উদঘাটিত করেছেন কবজির সমস্ত জোর ও হৃদয়ের সমবেদনা দিয়ে? হৃদয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করার চেষ্টা করেছেন কজন?
এই ব্যাপারে নিজের অভিজ্ঞতা এবং প্রত্যক্ষ সংযোগটাই বোধ হয় বড়ো কথা। কল্পনার বোধ হয় তেমন দাম নেই। যে, সে-জীবন নিজের চোখে না দেখেছেন অথবা যাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে ও মননে সে দরদ ও অন্তদৃষ্টি দূরদৃষ্টির সঙ্গে বিশেষভাবে ওতপ্রোতভাবে মিলেমিশে যায়নি তাঁর পক্ষে তিনি যে-সমাজের লোক নন সেই অন্য সমাজের কথা তেমন করে লেখা বা তুলে ধরা বড়োই কঠিন কাজ।
তা যদি না হত তাহলে রবীন্দ্রনাথের মতো কালজয়ী বহুমুখী প্রতিভাও এমন খেদোক্তি কেন করবেন? যদি কল্পনা দিয়েই দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠদের মনের কথা জানা যেত, শুধুমাত্র স্বার্থপ্রণোদিত নিজ নিজ উদ্দেশ্যসাধনের বক্তৃতা করেই তাদের হৃদয় হেঁওয়া যেত, তাহলে রবীন্দ্রনাথের পক্ষেও তা অসম্ভব বলে প্রতীয়মান হল কেন? কেন তাঁর মতো লোকও লিখতে বাধ্য হলেন :
কৃষাণের জীবনের শরিক যে জন,
কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন,
যে আছে মাটির কাছাকাছি,
সে কবির বাণী-লাগি কান পেতে আছি।
সাহিত্যের আনন্দের ভোজে
নিজে যা পারি না দিতে, নিত্য আমি থাকি তারই খোঁজে
সেটা সত্য হোক, শুধু ভঙ্গি দিয়ে যেন না ভোলায় চোখ
সত্য মূল্য না দিয়েই সাহিত্যের খ্যাতি করা চুরি।
ভালো নয়, ভালো নয় নকল সে শৌখিন মজদুরি।
কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা, মাটির কাছাকাছি থাকা এবং শুধু ভঙ্গি দিয়ে চোখ না ভোলানোর কথা আজকে ভাবতেও কষ্ট হয়। শুধু সাহিত্য কেন, অন্য প্রায় সব ক্ষেত্রেই আমাদের এমন সুন্দর সোনা-ছড়ানো দেশটাতে কর্ম ও কথার মধ্যে কোনোরকম সাযুজ্যই আজ আর না দেখি না, দেখি না কথা অথবা কর্মের মধ্যে মাটির গন্ধ। শুধু ভঙ্গিই আজকে সব। ভান ও ভন্ডামির তীব্র লজ্জাকর প্রতিযোগিতা দেখে দেখে যারা অসহায় নিরুপায় দর্শক হয়ে তা দেখেন তাঁরা নিজেরাই অন্যদের নির্লজ্জতায় লজ্জা পান। অথচ নির্লজ্জতায় কর্ম কী কঠিন। কিছুতেই, কোনো কিছুতেই, তাতে ফাটল ধরে না।
রবীন্দ্রনাথই বলেছিলেন, অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে, তব ঘৃণা তারে যেন তৃণ সম দহে। কিন্তু নিজেদের এমনই এক তুরীয় অবস্থায় উন্নীত করেছি আমরা নিজেদের এবং একমাত্র নিজেদেরই স্বার্থপরতায়, নিজ নিজ চাকরি ও ব্যবসায়ের কারণে যে, ঘৃণাবোধ বুঝি আর আমাদের মধ্যে অবশিষ্ট নেই। যদি তা থাকত, তাহলে নিজেদের প্রতি নিজেদেরই ঘৃণা আমাদের জ্বালিয়ে এতদিনে অঙ্গার করে দিত।
বাড়ির কাছাকাছি এসে গাড়ি হঠাৎ পথে একটা ছোটো গর্তে পড়ে লাফিয়ে উঠল। ইংরিজিতে যেরকম গর্তকে পট-হোল বলে।
সঙ্গে সঙ্গে টবী বলল, এখুনি গিয়ে কাউন্সিলরকে ফোন করতে হবে।
আমি অবাক হয়ে বললাম, কেন?
রাস্তায় গর্ত হয়েছে কেন? আমরা রোড-ট্যাক্স দিই না?
আমি বললাম, তাহলেও এত রাতে ভদ্রলোকের ঘুম ভাঙানোর কী দরকার?
টবী বলল, ঠিক আছে। না হয় কাল সকালেই করব।
করলে কী হবে? আমি শুধোলাম।
টবী বলল, দু-ঘণ্টার মধ্যে গর্ত মেরামত হয়ে যাবে।
তারপর কী ভেবে বলল, না কাল মনে থাকবে না, এখুনি করব। পাবলিক সার্ভেন্ট ওঁরা। কিছু মনে করবেন না।
আমি ও স্মিতা ওকে অনেক করে নিবৃত্ত করলাম।
পরদিন সকালে যখন প্রাতরাশ খেয়ে আমরা চরাবরায় বেরোলাম, তখন দেখি সত্যি সত্যিই গর্তটা মেরামত হয়ে গেছে।
আসলে ইংরেজরা বেনের জাত বলে দেনা-পাওনা সম্বন্ধে জ্ঞান এদের বড়োই টনটনে। যা দিল তা দিল, তা রোড ট্যাক্সই হোক কি ইনকাম-ট্যাক্সই হোক কিন্তু বদলে যা পেল তাও তারা বাজিয়ে নিতে ভোলে না। অ্যাকাউন্ট্যান্সিতে যে ডাবল-এন্ট্রি বলে কথাটা আছে তা ইংরেজদেরই সৃষ্টি। এ ডেবিট মাস্ট হ্যাভ আ ক্রেডিট। সিঙ্গল এন্ট্রিতে ইংরেজ বিশ্বাস করে না। তাই পাবলিক সার্ভেন্ট কাউন্সিলরকে দিয়ে দু-ঘণ্টার মধ্যে তারা পথের একটা সামান্য গর্ত সারিয়ে নিতেও ছাড়ে না। নিজের নিজের দায়িত্ব সম্বন্ধে যেমন এরা সচেতন, নিজের নিজের পাওনা সম্বন্ধেও তেমনি।
টবী সেদিন অফিস থেকে ফিরেই বলল, রুদ্রদা, তোমার কন্টিনেন্ট বেড়াবার সব বন্দোবস্ত করে এলাম আজ।
কীরকম?
টবী বলল, কসমস ট্যুরস-এর টিকিট কেটে এনেছি। তবে এটা কমোনারদের ট্যুর। তোমার বেশ কষ্ট হবে। কলকাতার জাদুঘরের সামনে সার দেওয়া ঘোড়ার গাড়ি থেকে নেমে রঙিন-শাড়ি পরা দক্ষিণ ভারতীয় তীর্থযাত্রীদের দেখেছ নিশ্চয়ই–এ ট্যুর অনেকটা সেরকম। ড্রাইভার-কামার-ছুতোর-সবজিওয়ালা মায় সবাই এই ট্যুরে বেরিয়ে পড়ে কন্টিনেন্ট দেখে আসে। আমি আর স্মিতা তোমাকে ভিক্টোরিয়া স্টেশনে তুলে দিয়ে আসব। সেখান থেকে ট্রেনে যাবে ডোভার। ডোভার থেকে জাহাজে ইংলিশ চ্যানেল পেরিয়ে বেলজিয়ামের অস্টেণ্ড। অস্টেণ্ড থেকে কসমসের কোচ করে বারো দিন সারা ইয়োরোপ প্রায় চরকি-বাজির মতো ঘুরবে।
আমি বললাম, ক্যানাডায় যাবার টিকিট কাটা আছে যে আমার!
আহা! ক্যানাডায় তো যাচ্ছই। আমি সে-সব বুঝে কেটেছি। ওই ট্যুর সেরে ফিরে এসে আরও দিন কয় এখানে থেকে গা-গতরের ব্যথা কমিয়ে নিয়ে তারপর টরোন্টো যেয়ে এখন। মাসতুতো ভাই কি পিসতুতো ভাই-এর শত্রু হতে পারে? তোমাকে আমি তার কাছে বিলক্ষণ পাঠাব।
তাহলে আমি আর ক-দিন আছি এখানে?
আরও সাতদিন আছ। টবী বলল।
তারপর বলল, তোমাকে আরও যা-যা দেখাবার তা দেখিয়ে দেব। তুমি তো আবার কারও হাত ধরে কিছুই দেখতে চাও না। নিজেই চরে-বরে যতটা পারা দেখে নাও সারাদিন। আমি সন্ধের পর তোমাকে রোজ কম্পানি দেব। আর ছুটির দিনে।
তথাস্তু। বললাম আমি।
আজ সন্ধেয় কী প্রোগ্রাম?
আজ তোমাকে Oh Calcutta দেখাতে নিয়ে যাব।
স্মিতা বলল, আমিও যাব।
টবী বলল, তুমি ভীষণ অসভ্য হয়েছ। শুধু এই সবই বোঝো। নিজের মগজে স্ক্র ঢোকালেও তো আর্ট-কালচার গলবে না। যার মন যেরকম।
টবী বলল, তুমি যাই-ই এল–তোমাকে ভাসুরঠাকুরের সঙ্গে ওই শো দেখাতে নিয়ে যাচ্ছি না।
স্মিতা বলল, তুমি ভীষণ গোঁড়া ও সেকেলে। এত বছর বাইরে থেকেও এত ওডোনাইজার মেখে এত সুগন্ধি সুগন্ধি সাবান ঘষেও তোমার গায়ের চেতলার গন্ধ মুছল না।
টবী দু-হাত ওপরে তুলে বলল, খবরদার ডার্লিং আর যাই করো চেতলা তুলে কথা বলবে না। চেতলা আমার কৈশোরের স্বপ্ন, যৌবনের উপবন…।
তারপর কী বলবে ভেবে না পেয়ে আমার দিকে ফিরে বলল, কিছু এল না রুদ্রদা! বিপদ থেকে ভাইকে একটু সাহিত্যিক বুকনি ছেড়ে উদ্ধার করো!
স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়াতে কখনো মাথা গলাতে নেই। আমাকে আমার এক অভিজ্ঞ বন্ধু বলে দিয়েছিল যে, ইচ্ছে করলে পথের দুই বিবদমান কুকুরের ঝগড়া মেটালেও মেটাতে পারো। কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া-নৈব নৈব চ। ওর মধ্যে গিয়ে পড়লেই দেখবে কিছুক্ষণ পর মিয়া বিবি দুজনের ঝগড়া মিটে গেছে–দুজনের মধ্যে গলাগলি–আর তোমার জন্যে যুগপৎ গলাধাক্কা।
অতএব চুপ করে থাকলাম।
Oh Calcutta সম্বন্ধে দেশে থাকতেও অনেক পড়েছিলাম ও শুনেছিলাম। তাই উৎসাহ নিয়েই দেখতে গেছিলাম, কিন্তু অগণ্য সম্পূর্ণ নগ্ন মানব-মানবী ছাড়া এর মধ্যে চমকপ্রদ আর কিছুই দেখলাম না।
আরম্ভটায় চমক আছে নিঃসন্দেহে। সেন্স অফ হিউমার আছে। টিপিক্যালি ব্রিটিশ সেন্স অফ হিউমার। কিন্তু যতই সময় যেতে লাগল ততই মনে হতে লাগল যে সাদা-মাটা কুদৃশ্য যৌন-বিকারকে একটা ইন্টেলেকচুয়াল পোশাক পরিয়ে দুর্বোধ্যতার গোঁফ লাগিয়ে যেন বাইরে আনা হয়েছে।
আজকালকার এই নব্য দুনিয়ায় যা-কিছু সরল সত্য ও সুন্দর এবং শাশ্বত তার সব কিছুই ফ্ল্যাট-সাদামাটা। তার মধ্যে যেহেতু সস্তা নতুনত্বের ভঙ্গুর চমক নেই সুতরাং এসব একেবারেই গ্রাহ্য নয়। পুরোনো যা-কিছু তা খারাপ, নতুন সব কিছুই যেন ভালো। যা-কিছু সহজে বোঝা যায়, হৃদয় দিয়ে ছোঁওয়া যায়, যা-কিছু বুকের মধ্যে আলোড়ন তোলে আমাদের মূল ভাবাবেগের কেন্দ্রে ঢেউ জাগায় তার সব কিছুই মূখামি, ছেলেমানুষি; সেন্টিমেন্টাল। এর বিপরীতটাই আজকালকার ফ্যাশান। ভোরের সূর্যের রং লাল বলেই তাকে নীল করে দেখানোটার নাম আধুনিকতা। যা-কিছুই সমস্ত বুদ্ধি জড়ো করেও বোঝা যায় না সেইটে না বুঝেও বোঝার ভান করাটাই বুদ্ধিমত্তার লক্ষণ।
একসঙ্গে অসংখ্য নগ্ন নারী-পুরুষ দেখতে এবং তাদের মিলনের দৃশ্য দেখতে সকলের ভালো লাগে না। আমার তো নয়ই। হয়তো কারও কারও ভালো লাগে। যাদের লাগত তাদের চিরদিনই লাগত। পৃথিবীর সব দেশেই যারা তা দেখতে চাইত এবং যাদের তা দেখার ইচ্ছা ও সামার্থ্য ছিল তা দেখে এসেছে কিন্তু গোপনে, লজ্জার সঙ্গে; হয়তো অপরাধবোধের সঙ্গেও। সেটায় কোনো আধুনিকতা নেই। কখনো ছিলো না। কিন্তু আজকে সেই লজ্জাবোধ ও শালীনতাবোধকে নষ্ট করাটাই, যা ছিল মুষ্টিমেয়র রুচি তাকে অপ্রত্যক্ষভাবে সার্বজনীন রুচিতে পরিণত করার এ চেষ্টাই সপ্রতিভ। আর এর বিরুদ্ধাচরণ করাটা প্রাগৈতিহাসিকতা, জড়ত্ব; স্থবিরতা।
Oh Calcutta ব্যাপারটা পুরোপুরি ন্যাক্কারজনক মনে হল। তবে এদের উদ্দেশ্যটাই খারাপ ছিল না। আমি যতটুকু বুঝেছি তাতে মনে হয়েছে যে পুরাতন সমাজের ও সমাজপতিদের ভন্ডামির মুখোশ ছিঁড়ে ফেলার চেষ্টাই ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু মুখোশটার প্রকৃতি যদি যথেষ্ট দৃঢ় হয় তাহলে তা ছিঁড়তে হলে দৃঢ় কবজির প্রয়োজন। শুধু তাই-ই নয়, মুখোশ ঘেঁড়ার প্রচেষ্টার মধ্যেই সমস্ত চেষ্টাটা ফুরিয়ে গেলে পুরো প্রচেষ্টাটাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য যদি না সেই মুখোশের আড়ালে প্রকৃত মুখকে প্রকাশ করা যায়। মুখোশের আড়ালে যদি কঙ্কালের মুখ দৃশ্যমান হয় বা জাদুঘরের যবনিকা রঙের মতো ঘন কৃষ্ণবর্ণ রং-ই চোখে পড়ে তাহলে মুখোশ ছেঁড়ার প্রয়োজনীয়তাটা কী তা বুঝি না। পূর্বসুরীদের ভন্ডামির মুখোশ ছিঁড়ে যদি নব্যদিনের ইন্টেলেকচুয়ালদের ভন্ডামির নতুন মুখোশই নতুন করে পরানো হয় তাহলে মুখোশ ঘেঁড়ার কোনো সার্থকতাই দেখতে পাই না।
তবুও বলব এদের উদ্দেশ্যর গভীরে মহৎ কিছু একটা ছিল। কিন্তু গভীরে কিছু উৎখাত করতে হলে যে বা যাঁরা উৎখাতের চেষ্টা করেন তাঁদেরও মূলত গম্ভীর হতে হয়। গভীরে যেতে হয়। বিদ্যা-বুদ্ধির অস্পষ্ট নখ দিয়ে খোঁড়াখুঁড়ি করে পুরাতন সংস্কার এবং ভন্ডামির মহীরূহকে রাতারাতি উৎপাটন করা যায় না–তার জন্যে সেই মহীরূহর শিকড় যতদূর অবধি পৌঁছেছে ততদূর অবধি পৌঁছোনোর মতো দীর্ঘ তীক্ষ্ণ প্রত্যয়ের নখরের প্রয়োজন।
এ ছাড়াও উদ্যোক্তারা এই অনুষ্ঠানের নাম যে কেন Oh Calcutta দিলেন তা ভেবে পেলাম না। অসলংগতাই অপ্রয়োজনীয় নিয়মবদ্ধতার একমাত্র প্রতিষেধক নয়। অসংলগ্ন নব্যতার মধ্যেও একটা নিয়মানুবর্তিতা থাকা দরকার। কারণ, চরম নব্যতাও অচিরে পুরাতন হয় যদি না সেই নব্যতার প্রয়োজনীয়তা ও অবিসংবাদিতা বিশেষ নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে দিয়ে প্রতিভাত হয়।
Oh Calcutta-অনুষ্ঠান থেকে বেরিয়ে আমরা পৌঁছোলাম গিয়ে পিকাডিলি সার্কাসে। এখানে রাত-দিনের তফাত নেই। বরং দিনের চেয়ে রাত যেন বেশি উজ্জ্বল। এরই পাশে পাশে Soho। লানডানের তরল আনন্দের উৎসস্থান। এখানে এমন এমন সব দোকান আছে। যে একজন সাধারণ ভারতীয়র চোখে তা আশ্চর্য ঠেকে। এসব জিনিস একটু রেখে-ঢেকেও করা চলতে পারত। কিন্তু সমস্ত পশ্চিমি পৃথিবী এখন তাবৎ ভন্ডামির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছে। মনে হয় এরা এখনও সম্যক বুঝতে পারেনি যে বাঘের পিঠে চড়ে বেড়ালে প্রথম প্রথম মজা যে লাগে না তা নয়; কিন্তু তার শেষ পরিণাম সুখপ্রদ নয়।
দোকানে লেখা আছে Sex Shop।
টবীর সঙ্গে ঢুকে চক্ষু চড়ক গাছ হয়ে গেল।
দোকানের জিনিসপত্র দেখে আমাদের থ হয়ে যেতে হয়। আমাদের ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিতে পুষ্ট হবার পর এমন সুন্দর ও পবিত্র ব্যাপারটাতে এমন কদর্যতার রং লাগানোর তাৎপর্য আমাদের পক্ষে বোঝা মুশকিল। আনন্দ যখন সৌন্দর্য, গোপনীয়তা ও শালীনতার মধ্যে দিয়েও পাওয়া যেতে পারে তখন সেই আনন্দর এমন বটতলা সংস্করণের কী প্রয়োজন তা বুঝে উঠতে পারলাম না।
এই সব সেক্স-শপ-এ নানাবিধ রাবার বা ওই জাতীয় জিনিসে তৈরি স্ত্রী-অঙ্গ বা পুরুষাঙ্গ বিক্রি হচ্ছে। নানা মাপের। রতিক্রিয়ার বিভিন্ন সাজ-সরঞ্জাম সার দিয়ে সাজানো আছে। স্ত্রী ও পুরুষের আত্মরতির যন্ত্রপাতিও আছে। যেন নারী ও পুরুষের মিলনে এবং একটি লেদ বা ড্রিলিং মেশিনের চলার প্রক্রিয়ায় কোনো তফাত নেই। মানুষের যেন শরীরটাই সব, সমস্ত কিছু; মন বলে যে পদার্থটি মানুষকে এত হাজার বছর পৃথিবীর অন্যান্য জীবদের থেকে মহত্তর করেছে সেই মনটির কোনো দামই ধরে না আজ মানুষ।
কালের ইতিহাসে একদিন আমরা এই পশ্চিমিদের থেকে অনেক বিষয়ে এগিয়ে ছিলাম। মাঝে এরা যান্ত্রিক সভ্যতা ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ক্ষেত্রে আমাদের পেছনে ফেলে অনেক দূর এগিয়ে গেছিল। দেশ স্বাধীন হবার পর আমরা এবং অন্যান্য অপর অনুন্নত দেশের লোকেরা তাদের সমকক্ষ হয়ে ওঠার চেষ্টা করছি দেখেই বোধহয় তারা এমন এমন ব্যাপারে আমাদের চমকে দিতে চাইছে যে, সে চমক থেকে চোখ ফেরানোই বুদ্ধিমানের কাজ।
আমরা এদের চেয়ে অনেক গরিব। ছেঁড়া কাপড় পরি আমরা, ভালো খেতে পাই না, কিন্তু অনেক ব্যাপারে যে আমরা এদের চেয়ে অনেক বেশি ধনী এটা ওদের আজকের যুগের ছেলে-মেয়েরা খোঁজ রাখে না। দুঃখ তাতেও ছিল না। বড়ো দুঃখ হয় যখন দেখি যে, আমাদের নিজের দেশের ছেলে-মেয়েরাও একথা ভুলে গিয়ে ওদের এই সস্তা চটকের অনুকরণে নিজেদের সম্পূর্ণভাবে ডুবিয়ে রাখে। বর্তমানে আমাদের দেশের বিত্তবান শ্রেণির ছেলে-মেয়েদের পোশাক-আশাক মানসিকতা ইত্যাদির সঙ্গে এই দেশের ছেলে-মেয়েদের পোশাক-আশাক মানসিকতার বিশেষ তফাত দেখি না। দেশের সবচেয়ে বড় দুর্যোগ এটা। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক কোনো দুর্যোগই এই নৈতিক দুর্যোগের সঙ্গে তুলনীয় নয়।
সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান একবার পি-ই-এন কংগ্রেসের বক্তৃতায় লেখকদের উদ্দেশ করে বলেছিলেন :
It is a familiar conception of Indian thought that the human heart is the scene between good and evil. It is assailed by weakness and imperfection but is capable also of high endeavour and creative effort. Man is a composite of life giving and death-dealing impulses. As the Wrig Veda puts it.
যস্য ছায়া অমৃতম যস্য মৃতম।
The Mahavarata says : Immortality and Death are both lodged in the nature of man. By the pursuit of Moha or delusion he reaches death, by the pursuit of truth he attains immortality. We are all familiar with the verse in Hitopodesa that hunger, sleep, fear and sex are common to men and animals. What distinguishes man from animals is the sense of right and wrong, life and death, love and violence, are warring in every struggling man.
হিতোপদেশের সেই শ্লোকটি উনি উদ্ধৃত করেছিলেন :
আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনম,
কা সামান্যমে তাৎ পশুভিরনরানাম
ধর্ম হি তেষাম অধিকো বিশেষো,
ধর্মেনা হীনা পশুভি সমানাঃ।
এই ধর্মই হচ্ছে মানুষের ধর্ম। পশুর ধর্ম নয়।
পিকাডিলি সার্কাসের পিছনে অনেক গলি খুঁজি। কেমন একটা থমথমে ভাব। বেসমেন্টে ও ওপরে নানারকম ঘোঁৎ-ঘোঁৎ। বেটন হাতে লানডানের পুলিশরা কোটের কলার তুলে ঠাণ্ডায় ঘুরে বেড়াচ্ছে।
নানারকম রং-এ রং-করা চুল নিয়ে সেজে-গুঁজে উগ্র সুগন্ধি মেখে সুন্দরী অসুন্দরী মেমসাহেব বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে। অনেক পুরুষ বিভিন্ন জায়গায় দাঁড়িয়ে নানারকম লোভনীয় সব অনুষ্ঠানের কথা ঘোষণা করছে।
টবী বলল, বুঝলে রুদ্রদা, এই-ই হল গিয়ে Soho পাড়া।
বুঝলাম, বললাম আমি।
হঠাৎ টবী একটা বড়ো দামি কথা বলল। লাখ কথার এককথা। এ কথাটা আমার মনেও ছিল ছোটোবেলা থেকে কিন্তু মনের অভ্যন্তরেও কখনো এমন করে একথাটার প্রাঞ্জল অভিব্যক্তি প্রস্ফুটিত হয়নি।
টবী বলল, এসব জায়গায় কারা আসে জানো রুদ্রদা?
কারা? আমি শুধোলাম।
যারা, সোশ্যালি কনডেমড।
কথাটা বড়ো জুতসই মনে হল। সত্যিই তো। সমাজ থেকে যাদের কিছুমাত্র পাওয়ার আছে, আশা করার আছে, তারা নিজেদের এমনভাবে ছোটো করবে কেন? যা তারা এমনিতে পেল না, নিজের রূপে পেল না, গুণে পেল না, মানে-সম্মানে কিছুতেই পেল না তারা পয়সার বিনিময়ে এমন ঘৃণার সঙ্গে ঘৃণার মধ্যে তা পেতে যাবে কেন? যা নরম গোপন সহজ আনন্দর দান তা আবরণহীন নির্লজ্জতার দেনা-পাওনার মধ্যে আশা করবে কেন?
টবীকে বললাম, জব্বর বলেছিস টবী।
টবী বলল, কী জানি? আমার চিরদিনই এমন মনে হয়েছে। বিশেষ করে যত বছর ইয়োরোপে আছি। এখানে এসব ব্যাপারে এতখানি স্বাধীনতা–প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রী-পুরুষ এতখানি স্বাধীন যে সুস্থতার মধ্যেই তারা সব কিছু সহজে পেতে পারে, চুরি করে অসুস্থতার মাধ্যমে কিছু পাওয়ার তাদের দরকার কী? তবুও, সব দেশেই বোধহয় এক ধরনের লোক থাকেই–অসুস্থতা ও বিকারগ্রস্ততাই বোধহয় তাদের ধর্ম। যা মাথা উঁচু করে পাওয়া যেতে পারত, তা মাথা হেঁট করে পেতেই বোধহয় তারা ভালোবাসে।
টবীর গাড়িটা পার্ক করানো ছিল দূরে। আমরা সেখানে হেঁটে গিয়ে গাড়িতে উঠলাম। ঠাণ্ডাটা বেশ ভালো পড়েছে। আমার পক্ষে তো বটেই।
টবী বলল, চলো তোমাকে প্লে-বয় ক্লাবে নিয়ে যাই।
আমি বললাম, সেটা কী ক্লাব?
ও অবাক হল। বলল হিউ-হেফনারের নাম শোনোনি?
না। আমি বোকার মতো বললাম।
প্লে-বয় ম্যাগাজিন দেখেছ কখনো?
আমি বললাম, হ্যাঁ। তা দেখেছি। নানারকম গা-গরম করা ছবি-টবি থাকে।
টবী বলল, তাহলে তো দেখেছ। হিউ-হেফনার অ্যামেরিকান। প্লে-বয় ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা। পৃথিবীর বহুজায়গায় এই ক্লাব আছে। খুব একসকুসিভ ক্লাব। মেম্বারশিপ বেশ লিমিটেড। চলো তোমাকে দেখিয়ে আনি।
দেখতে দেখতে আমরা লানডানের অভিজাত পাড়া মে-ফেয়ারে এসে পড়লাম। মে ফেয়ারের পার্ক লেনে প্লে-বয় ক্লাব।
ক্লাবটা যে খুব বড়ো তেমন নয়। ছোট্ট এনট্রান্স–বাইরে থেকে দেখে বোঝাই যায় না যে ক্লাব।
ভেতরে ঢুকতেই ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলাম। দেখি অতিসুন্দরী অল্পবয়েসি মেয়েরা প্যান্টির ওপর সুইম স্যুটের চেয়েও অনেক হ্রস্ব গরম পোশাক পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মেম্বারদের খাদ্যপানীয় সরবরাহ করছে। তাদের প্রত্যেকের পশ্চাৎদেশে একটি সাদা ফারের বল মাথায় খরগোশের কানের মতো ভেলভেটের কান। তাদের নাম Bunny.
Bunny Girl-রা সারাপৃথিবীতে বিখ্যাত।
টবী ওপরে নিয়ে গেল আমাকে। দেখি সেখানে সিগারেট আর পাইপের ধোঁয়ায় অন্ধকার হয়ে আছে। আর নানারকম টেবিলের চারপাশে নারী-পুরুষ ভিড় করে ঝুঁকে রয়েছে। বিভিন্ন আকৃতির বিভিন্ন প্রকৃতির জুয়াখেলার বোর্ড।
এ ব্যাপারটা আমি কখনো ভালো বুঝি না। ভালো মানে, একবারেই বুঝি না। ঘরের মধ্যে বসে যেসব খেলা যায় সেসব খেলা ছোটোবেলা থেকেই বাবার কড়া শাসনে শেখা হয়নি। শেখা যে হয়নি তার জন্য নিজের বিন্দুমাত্র দুঃখ নেই বরং স্বস্তি আছে। পাঠক হয়তো শুনলে অজ্ঞানও হয়ে যেতে পারেন যে তাস পর্যন্ত চিনি না আমি–খেলা জানা তো দূরের কথা। জুয়া তো আরও দূর।
সে-কারণেই এখানে এসে বিশেষ বুঝতে পারলাম না চতুর্দিকে কী ঘটছে না ঘটছে। তবে সমবেত জনমন্ডলীর মুখ-চোখের ভাব দেখে মনে হল তাঁদের উৎসাহের অন্ত নেই।
এক জায়গায় দেখি কয়েকজন আমাদেরই মতো কালো-কালো লোক গালে হাত দিয়ে তন্ময় হয়ে বসে দানের পর দান দিয়ে যাচ্ছে। উঁকি মেরে দেখি যে-চাকাটা ঘুরছে তার ওপর লেখা আছে–মিনিমাম স্টেক–দুশো পাউণ্ড।
দেখেই আমার মাথা ঘুরে গেল। বুঝলাম না এরা কারা? কোন গ্রহের লোক? শুনেছি অ্যামেরিকানরা ও জাপানিরা খুব বড়োলোক। কিন্তু এদের চেহারা প্রায় আমারই মতো দিশি দিশি–কিন্তু এক এক দানে চারহাজার টাকা নষ্ট করছে এরা কারা? শুধু তা-ই নয়, দেখি Bunny গার্লরা তাদের ক্রমাগত রয়্যাল-স্যালুট স্কচ হুইস্কি পরিবেশন করে যাচ্ছে। যে হুইস্কির একবোতলের দাম স্কটল্যাণ্ডেও কম করে হাজার টাকা। আমার মুখ-চোখ লক্ষ করে, পাছে আমি অজ্ঞান হয়ে যাই–তাই তাড়াতাড়ি টবী বলল, এরা সব তেল-দেওয়া লোক।
আমি বুঝলাম না। বললাম, মানে?
টবী বলল, আবু দাবি, দুবাই এসব জায়গার অয়েল-ম্যাগনেট এরা–লানডানে ফুর্তি করে যাচ্ছে।
আমি উত্তেজিত গলায় বললাম, তেল-বেচা টাকা দিয়ে? কোনো মানে হয়? আর তেলের খরচের জন্যে আমি টেনিস খেলা বন্ধ করে দিয়েছি তেলের দাম বাড়ার পর থেকে।
টবী বলল, এখন তো এদেরই দিন।
সে-রাতে ফিরতে ফিরতে অনেক রাত হয়ে গেল।
টবীর সঙ্গে কথা হচ্ছিল যে স্কটল্যাণ্ড দেখা হল না।
টবী বলল, তুমি দু-মাসে তামাম পৃথিবী দেখবে বলে বেরিয়েছ তার আমি কী করব? পরের বছর আবার চলে এসো। শুধু টিকিটের খরচ তোমার। শুধু একমাসের জন্যে এসো। আমি যতদিন পারি আগে থেকে ছুটি ম্যানেজ করব। গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ব। তোমাকে স্কটল্যান্ড আর জার্মানি ভালো করে ঘুরিয়ে দেখাব। বহু বন্ধু-বান্ধব আছে। তোমার তো কোনোই খরচ নেই–শুধু ছুটি নিয়ে আসা।
আমি হাসলাম। বললাম, এবারই বা কী খরচ? দেশে দেশে এমন সব রেস্তদার ভাই বিরাদর থাকতে আমার আর ভাবনাটা কী?
টবী বলল, স্কটল্যাণ্ড তোমার খুব ভালো লাগবে। স্কটিশ মুরস, লেকস আর পাহাড়গুলো। ভেজা ভেজা মেঘ-মেঘ।
আমি বললাম, আমার কলকাতায় এক স্কচ বন্ধু ছিল, সে ব্রিটিশ এমব্যাসিতে ছিল– বরাবর আমায় নেমন্তন্ন করত হ্যাগেস দেখতে। পুরোপুরি স্কটল্যাণ্ডের পোশাক পরে ওরা ওদের বাড়িতে যে হুল্লোড় করত তা বলার নয়। স্কচ লোকেরা কিন্তু ভারি দিলখোলা হয়, তাই না?
টবী বলল, যা বলেছ। কিন্তু কিপটে হয়।
স্মিতা বলল, রুদ্রদা, তোমার দিন তো ফুরিয়ে এল। এবার তুমি মাদাম তুসোর গ্যালারি আর ব্রিটিশ মিউজিয়মটা ভালো করে দেখে নাও।
বললাম, হ্যাঁ। লাইব্রেরিতেও যেতে হবে। তারপর বললাম, আসলে কী জানো লাইব্রেরি, মিউজিয়ম এমন করে দেখা যায় না। দেখলে ভালো করেই দেখতে হয়। নইলে কলকাতা ফিরে আম্মো দেখেছি বলা ছাড়া আর কোনো লাভ হয় না। আমি বিদেশে এসেছি অন্য কাউকে বিন্দুমাত্র ইমপ্রেস করার জন্যে নয়–নিজে ইমপ্রেসড হতে। নিজে যা ভালো করে দেখতে পেলাম তা দেখে লাভ কী? কলকাতার ককটেল পার্টিতে হুইস্কির গ্লাস হাতে করে দাঁড়িয়ে অনেকে যেমন দেশ বেড়ানোর গল্প করেন আমি সেইরকম দেশ বেড়ানোতে বিশ্বাস করি না। তাই তো এই স্বল্প সময়ে যতটুকু পারছি লোকজনের সঙ্গে মেশার চেষ্টা করছি। দু চোখ দু-কান ভরে ওদের কাছে কী শেখার আছে তাই-ই শেখার চেষ্টা করছি এই সময়ের মধ্যে। এ সময়ে কিছুই হবে না জানি, তবুও যতটুকু হয়। নাই-মামার চেয়ে কানা-মামা ভালো।
আমরা বসে ড্রইংরুমে গল্প করছি। খাওয়া হয়ে গেছে আমাদের। টেলিভিশনে একটা ফিচার-ফিল্ম দেখাচ্ছে। স্মিতাই দেখছে একা। এমন সময়ে টেলিফোনটা বাজল।
টবী ফোন ধরেই বলল, রুদ্রদা, সানুর ফোন, টরোন্টো থেকে।
সানু বলল, মুশকিল হল। আমার ছুটির দরখাস্তটা মঞ্জুর হয়েছে কিন্তু আগে থেকে। তারপর আমাদের ইয়ার-ক্লোজিং। ছুটি পাব না। তোমার প্রোগ্রামটা একটু অ্যাডভান্স করে চলে এসো।
আমি বললাম, টবী যে কসমস-এর টিকিট কেটে ফেলেছে।
সানু বলল, লানডানে বসে বোরড হচ্ছ কেন? এক্ষুনি চলে যাও কন্টিনেন্টাল ট্যুরে। যে। তারিখে বলছি সে তারিখে চলে এসো। ফ্লাইট-নম্বরটা টবীকে বোলো ফোন করে জানিয়ে দেবে। আমি এয়ার-পোর্টে থাকব।
আমি বললাম, আছিস কেমন?
ও বলল, ফাইন। তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি। তাড়াতাড়ি এসো-নইলে ক্যানাডাতে ঠাণ্ডা পড়ে যাবে–ঘোরাঘুরির অসুবিধা।
বললাম, ঠিক আছে।
টবী বলল, নো প্রবলেম! তাই-ই করো।
স্মিতা বলল, সে হলে তো রুদ্রদাকে এর মধ্যে একদিন সাফারি পার্কে নিয়ে যেতে হয়। শিকারি মানুষ। ভালো লাগবে।
আমি হাসলাম। বললাম, দেখো স্মিতা, টবীর মতো শহরের শিকারে আনসাকসেসফুল বলেই জঙ্গলের শিকারি আখ্যা পেয়ে এলাম চিরদিন। তা বলে কি তুমি শিকারি বলে হেলা করবে?
স্মিতা বলল, ও যা শিকারি, জানা আছে। শিকার একটাই করেছে জীবনে–এই আমি। তাও আমি প্রায় আত্মহত্যা করলাম বলেই পারল, বাঁচতে চাইলে পারত না।
টবী উত্তর দিল না, সঙ্গে সঙ্গে কসমসের অফিসে ফোন করার জন্যে ডায়াল ঘোরাল।
সেদিন শনিবার ছিল। ছুটি। সকাল সকাল ব্রেকফাস্ট করে আমরা বেরিয়ে পড়লাম সাফারি পার্ক-এর উদ্দেশে।
ইটনের পথে কিছুদূর গিয়ে আমরা ঘুরে গেলাম। আধ ঘণ্টাটাক লাগল পৌঁছোতে। বিরাট এলাকা জুড়ে একজন সার্কাসের মালিক এই ওপেন-এয়ার চিড়িয়াখানা বানিয়েছে। বেবুন, বাঘ ও সিংহ আছে। সব ভোলা। তাদের মধ্যে দিয়ে আস্তে আস্তে গাড়ি চালিয়ে দেখতে হয়। বাইরে নোটিশ দেওয়া আছে যে, যার যার নিজের দায়িত্বে আগন্তুকরা ভেতরে ঢুকছেন –মাল-জানের দায়িত্ব যার-যার তার-তার। কতৃপক্ষ দায়ী থাকবেন না কিছু অঘটন ঘটে গেলে।
বেবুনগুলো বেশ বড়ো বড়ো। পশ্চাৎদেশ রক্তিমবর্ণ–সম্মুখভাগে দাঁত খিচোনো ভঙ্গি। গাড়ি দেখলেই গাড়ির মাথায় ফ্রি-রাইডের জন্য চড়ে বসে।
বেবুনদের এলাকা পেরিয়ে বাঘেদের এলাকায় এলাম। ছোটোবেলা থেকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জঙ্গলে ঘুরেও কখনো এমন এমন দৃশ্য দেখা যায়নি। কখনো দেখা যেত বলে মনেও হয় না। কারণ, বাঘ স্বাধীনচেতা ও রাজারাজড়া জানোয়ার। তারা যুথবদ্ধতায় কখনোই বিশ্বাসী নয়। তাই একসঙ্গে পনেরো-কুড়িটা বাঘকে একটি ছোটো এলাকার মধ্যে দেখে অবাকই হতে হয়।
জঙ্গলে একসঙ্গে কেন এত বাঘ দেখা যায় না তা একটু প্রাঞ্জল করে বলি। প্রথমত আগেই বলেছি বাঘ যুথবদ্ধ জানোয়ার নয়। দ্বিতীয়ত বাঘ ও বাঘিনি বছরের পুরো সময় কখনোই একসঙ্গে থাকে না। বছরে তাদের দুবার মিলনকাল। সেই সময়ে সঙ্গী জুটিয়ে নেয়। খুব একটা বাছবিচারের সুযোগ পায় বলে মনে হয় না। যে-বছর যার সঙ্গে দেখা হয়ে যায় সে-ই সঙ্গী বা সঙ্গিনী হয়। সেই সময়ও প্রায়শই দেখা যায় যে, বাঘ ও বাঘিনি সন্ধে হতে না হতেই শৃঙ্গার শুরু করে রাত্রিশেষ অবধি মিলিত হয়। কিন্তু ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতে আলাদা-আলাদা হয়ে ঘুমোয়। কেউ গুহায়, কেউ-বা নালার নরম বালিতে। গরমের দিনে ছায়াচ্ছন্ন জায়গায়, শীতের দিনে রোদে, কিন্তু আড়ালে। অবশ্য এর ব্যতিক্রম যে হয় না এমন নয়।
বাঘেদের দাম্পত্যজীবন ভালোভাবে লক্ষ করলে অনেক কিছু শিখতে পারে মানুষ। বিবাহিত ব্যক্তিমাত্রেরই পাখা জোরে চালানো অথবা আস্তে চালানো, অথবা মশারি টানানো কিংবা না-টানানো নিয়ে বিস্তর মনকষাকষি হয় স্বামী অথবা স্ত্রীর সঙ্গে। বাঘেরা বুদ্ধিমানের মতো এসব ঝামেলা এড়িয়ে চলে।
হঠাৎ একটি বাঘিনি চটে উঠে ঘাড়ের লোম ফুলিয়ে ডেকে উঠল। সঙ্গে সঙ্গেই ওয়ার্ডেনের গাড়ি এসে আমাদের পাশে দাঁড়াল। খোলা ছোটো ভ্যান। তাতে জনচারেক ওয়ার্ডেন–দু কোমরে হেভিববারের দুই পিস্তল গুঁজে রয়েছেন প্রত্যেকে। হাতে লম্বা চাবুক।
কিন্তু তাঁদের হাবভাব দেখে মনে হল প্রত্যেক বাঘকেই তাঁরা চেনেন এবং নাম ধরে ডাকেন। তাঁরা এসে বাঘেদের বোধ্য ও আমাদের কাছে সবিশেষ দুর্বোধ্য কী ভাষায় বিস্তর অনুরোধ-উনুরোধ করায় বাঘিনি সরে গেল।
স্মিতা অস্ফুটে বলল, ইশ, তোমার কী সাহস, রুদ্রদা! এইরকম বাঘ তুমি পায়ে দাঁড়িয়ে মারতে পারো?
টবী বলল, রুদ্রদা আর কী সাহসী? আমি এর চেয়েও হিংস্র বাঘিনি নিয়ে দিনরাত ঘর করছি।
খবরদার! বলে স্মিতা ফোঁস করে উঠল।
আমি মাঝে পড়ে বললাম, বাঘ-বাঘিনি থাক, এবার সিংহের কাছে যাওয়া যাক।
এই সাফারি পার্কেও গত ইংরিজি বাহাত্তর সাল থেকে চুয়াত্তর সালের মধ্যে বাষট্টিটি সিংহের বাচ্চার জন্ম হয়েছে। ষাট, ষাট। মা-ষষ্ঠীর এমন দয়া! অনেক বাচ্চা নিশ্চয়ই বিক্রি হয়ে গেছে। অনেক বাচ্চা সার্কাসে ভরতি হয়ে এখন টুলের ওপর দাঁড়িয়ে খেলা দেখাচ্ছে। বর্তমানে পার্কে ছোটো-বড়ো মিলিয়ে প্রায় পঞ্চাশটি সিংহ-সিংহী আছে।
টবী বলছিল, সিংহগুলো মাঝে মাঝে গাড়ির ছাদে চড়ে পড়ে।
বলিস কী, বলতে বলতেই, একটা প্রকান্ড বড়ো ঘাড়ে-গর্দানে কেশর-ঝোলানো সিংহ আমাদের সামনে সামনেই যে একটা বাদামি-রঙা ফরাসি দেশীয় সিমকা গাড়ি যাচ্ছিল, তার বনেটের ওপর লাফিয়ে উঠল। যে ভদ্রলোক চালাচ্ছিলেন, তিনি প্রায় কেঁদে ফেললেন। পাশে সুন্দরী সঙ্গিনী–গাড়িটাও নতুন। সিংহ বোধহয় বেছে বেছে সে-কারণেই তার ওপর চড়ল। কিছুক্ষণ বনেটের ওপর দাঁড়িয়ে ভার সয় কি না দেখে নিয়ে বনেট থেকে আস্তে আস্তে গাড়ির ছাদে সামনের দু-পা বাড়িয়ে সাবধানে উঠল। যাতে পা না পিছলোয় সেই জন্যে। তারপর চাইনিজ ফিলসফারের মতো মুখভঙ্গি করে নট-নড়নচড়ন নট কিছু হয়ে বসেই থাকল।
আমরা দেখলাম, আস্তে আস্তে চকচকে সিমকা গাড়িটার ছাদ বসে যাচ্ছে। একটা প্রমাণ সাইজের হৃষ্টপুষ্ট সিংহের ওজন কম নয়।
চতুর্দিক থেকে পটাপট ছবি উঠতে লাগল। কিছুক্ষণ পোজ দিয়ে বসে থেকে তিনি একলাফ দিয়ে নেমে পড়লেন। তখন আমরা আস্তে আস্তে সিংহের এলাকা ছেড়ে গেটের দিক যেতে লাগলাম।
এদিকে-ওদিকে অনেক শকুন দেখলাম। এই বাঘ-সিংহদের যে খাবার দেওয়া হয়, সেই হাড়-গোড় ও তৎসংলগ্ন মাংসর সদ্ব্যবহার করে তারা।
সাফারি পার্কের ক্যান্টিনে এককাপ করে কফি খেয়ে আমরা বাড়ির দিকে ফিরলাম।
দুপুরটা সেদিন ভালো আড্ডা মেরে কাটল। স্মিতা পাবদা মাছের ঝোল বেঁধেছিল ধনেপাতা দিয়ে। রান্না ফার্স্ট ক্লাস হয়েছিল কিন্তু টাটকা পাবদা মাছ আর ডিপ-ফ্রিজে রাখা পাবদা মাছের স্বাদ সম্পূর্ণ আলাদা। তা ছাড়া বোধহয়, ইংল্যাণ্ডে বসে পাবদা মাছ ঠিক জমে না। যেখানকার যা; যখনকার তা।
বিকেল হতে-না হতে স্মিতা বলল, আমার এক বান্ধবী আসবে আজ সন্ধের সময়ে। তোমরা থেকো কিন্তু।
টবী শুধাল, কে বান্ধবী?
সুসান। স্মিতা বলল।
টবী বলল, আমি মোটেই থাকছি না। তা ছাড়া মেয়েটার সঙ্গে তোমার এত ঘনিষ্ঠতা ভালো নয়।
কেন? স্মিতা রাগত স্বরে শুধাল। টবী বলল মেয়েটা সুবিধের নয়। তোমাকে বলেছে। স্মিতা বলল।
তারপর বলল, এরকম মেয়ে আমি আমার পুরো অফিসে একজনও দেখিনি–কী ছেলেমানুষ আর কী যে ভালো!
টবী কথা ঘুরিয়ে বলল, থাক বাবা, আই উইথড্র। তবে, তোমার বন্ধু আসবে ভালো কথা, তুমি entertain করো। সুসান আসলে বোলো, আমি আমার কাজিনকে নিয়ে ডেন্টিস্ট-এর কাছে গেছি। দাঁতে রুদ্রদার খুব ব্যথা।
স্মিতা খুব মনমরা হয়ে বলল, সে কী? সুসান যে রুদ্রদার সঙ্গে আলাপ করার জন্যই আসছে। লেখক শুনে ও খুব আলাপ করতে উৎসুক। ও মাঝে মধ্যে ছোটো গল্প-টল্প লেখে।
টবী বলল, তাহলে লেখক বলে কি দাঁতে ব্যথা হতে পারে না?
তারপর একটু থেমে বলল, সুসানকে এক্ষুনি ফোন করে এল যে, লেখকের দাঁতে ব্যথা; যন্ত্রণায় কাত্রাচ্ছে কাটা-কইয়ের মত!
রিসিভারটা তুলে স্মিতা বলল, কাটা-কই-এর মতোর ইংরিজি কী?
টবী স্মিতার মুখের দিকে একদৃষ্টে অনেকক্ষণ চেয়ে বলল, কাটা-কই-এর মতো বলার দরকার নেই।
আমরা তিনজনেই একসঙ্গে হেসে উঠলাম।
কিন্তু সুসান তবুও আসবে বলল। আজ সন্ধেতে ও আর কোনো অ্যাপয়েন্টমেন্ট রাখেনি। স্মিতার সঙ্গে গল্প করবে আর খাবে–লেখকের সঙ্গে নাই-ই বা দেখা হল।
বলাবাহুল্য, একথাতে অধম লেখক মোটেই খুশি হল না। উত্তম লেখক হলেও সুসান আসার অনেক আগেই টবী আমাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।
লিফট থেকে নেমে গাড়িতে উঠতে উঠতে টবীকে বললাম যে, যতদুর মনে পড়ে তোর সঙ্গে কখনো কোনো শত্রুতা করিনি। কিন্তু একজন সুন্দরী সাহিত্যরসিকা উৎসুক তরুণীর সঙ্গে আমার আলাপে তোমার এহেন আপত্তি কেন?
টবী বলল, আই অ্যাম সরি। কিন্তু না-পালিয়ে উপায় ছিল না। আমি বাড়ি থাকলে কেস গড়বড় হয়ে যেত।
ব্যাপারটা কী? আমি শুধোলাম।
আরে ওর বড়ো বোন আমার গার্ল ফ্রেণ্ড ছিল। আমি সুসানের নাম শুনে এবং ওর বাবা মা কোথায় থাকে তা শুনেই বুঝেছি প্রথম দিন থেকে। ও আমাকে ভালো চেনে।
আমি বললাম, তুই নিশ্চয়ই কিছু অপ্রীতিকর কাজ করেছিলি।
টবী বলল, বিশ্বাস করো, আমি কোনো কিছুই করিনি। কিন্তু সুসানের দিদি আইলীন যে এমন ইমোশনাল, এত বেশি সেনসিটিভ তা বুঝতে পারিনি। ওদের পরিবারটি খুব ভালো। যেমন মা, তেমন বাবা। বাবা ইংরিজির অধ্যাপক ছিলেন এক মফসসল কলেজে। মেয়েরা সকলেই একটু কবি-প্রকৃতির। কী বিপদে যে পড়েছিলাম, কী বলব। আমি তাকে বিয়ে করব না, করা সম্ভব নয় বলাতে তার মাথার গোলমাল হয়ে গেছিল। এখন অবশ্য সব ঠিক-ঠাক হয়ে গেছে।
আমি বললাম, বিয়ে করলি না কেন? খুবই অন্যায় করেছিস।
টবী বলল, তুমি তো আজব লোক; বাবা খড়ম-পেটা করতেন না? মা কি মেমসাহেব ঘরে তুলতেন? তা ছাড়া বিয়ে করলে দিশি মেয়েই ভালো। এদের নিয়ে হিমসিম খেতে হয়।
এতই যদি জানিস তাহলে ইংরেজ মেয়ের সঙ্গে তেমনভাবে মিশলি কেন? প্রেম করলি কেন?
গাড়িটা সোয়ান-ট্যাভার্ন বলে একটা পাব-এর সামনে দাঁড় করাল টবী। গাড়ি পার্ক করে আমরা নামলাম।
টবী বলল, জানো এ পাবটা দুশো বছরের পুরোনো পাব। বিখ্যাত পাব এটা।
আমি বললাম, রাস্তাটা চেনা চেনা লাগছে যেন!
টবী বলল, লাগবেই তো। এটাই তো বেজওয়াটার স্ট্রিট। খুব লম্বা রাস্তা। বিয়ার মাগে গিনেস। কালো বিয়ার নিয়ে আমরা বাইরের খোলা আকাশের নীচের কাঠের তৈরি বসার জায়গায় এসে বসলাম।
চারপাশে ফুটফুটে সব ছেলে-মেয়ে। হুল্লোড় করছে, জোড়ায়-জোড়ায় ফিরে যাচ্ছে–মনে হচ্ছে জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত এই বুঝি ফুরিয়ে গেল ভেবে প্রচন্ডভাবে উপভোগ করে নিচ্ছে। আঁজলা গড়িয়ে যেন ছিটেফোঁটাও না পড়ে যায় জীবন। সবসময়ে সেদিকে নজর।
এদেশে এসে অবধি বারবারই মনে হয়েছে বয়েসটা কেন পঁচিশের নীচে হল না, কেন এদেশে পড়াশুনো করলাম না।
এসব কেন সকলের মনেই ওঠে–কিন্তু এসব কেনর কোনো উত্তর হয় না। হবে না। জানি, তবুও মনটা হঠাৎ হঠাৎ খারাপ লাগে। ভীষণ খারাপ।
কিন্তু জীবনে আর সবই হয়, কিন্তু জীবনের গাড়ির কোনো ব্যাক-গিয়ার নেই। এ গাড়ি শুধু সামনেই চলে। শুধুই সামনে।
ব্ল্যাক-বিয়ারের মাগ-এ একটা বড়ো চুমুক লাগিয়ে টবী হঠাৎ পথের দিকে চেয়ে চুপ করে গেল।
পথ দিয়ে বেশি গাড়ি যাচ্ছে না। শনিবারের রাত। এখন ভিড় বেশি হয় শুক্রবার রাতে। ফাইভ-ডেজ উইক হয়ে গিয়ে জীবনযাত্রার পুরোনো প্যাটার্ন বদলে গেছে।
আমিও পথের দিকে চেয়েছিলাম। ভাবছিলাম, বেশ কটা দিন কেটে গেল লানডানে টবীদের আতিথেয়তায়। ছোটোবেলায় কখনো ভাবিনি যে বেড়াতে আসব এখানে। ভেবেছিলাম কি না মনে পড়ে না। কিন্তু আমি বড়ো কৃতজ্ঞ লোক। এ জীবনে যা-কিছু পেয়েছি, যতটুকু পেয়েছি, অর্থ, যশ, ভালোবাসা, প্রীতি সব কিছুর জন্যেই সৃষ্টিকর্তার কাছে বড়ো কৃতজ্ঞ থাকি। যখনই একটু একা বসে ভাবার অবকাশ ঘটে, তখনই কৃতজ্ঞতার সঙ্গে বলি, ঈশ্বর! তুমি সত্যিই করুণাময়। যা পেয়েছি তার জন্যে আনন্দিত থাকি। যা-পাইনি সেইসব অপ্রাপ্তিজনিত নিখাদ দুঃখ দেওয়ার জন্যেও তাঁর কাছে বড়ো কৃতজ্ঞ থাকি। শুধু আমার একার কেন, সকলের সব খাদ তো দুঃখের আগুনেই ঝরে। যে দুঃখ পেল না, দুঃখকে আপন অন্তরের অন্তরতম করে জানল না, তার কাছে তো সুখের স্বরূপও অজানা। যে দুঃখকে জেনেছে, সেই-ই তো সুখকে জানতে পারে।
ভাবছিলাম দু-একদিনের মধ্যেই চলে যাব। আবার আসতে পারব কি না কে জানে? এসে যে ভারত উদ্ধার অথবা নিজেকে উদ্ধার করলাম এমন নয়। তবে, কত কী দেখলাম দু-চোখ ভরে, মানুষ দেখলাম, তাদের সমস্ত মন দিয়ে বোঝবার চেষ্টা করলাম, কথা শুনলাম। এটা একটা বড়ো শিক্ষা হল। পৃথিবীটা এতদিন যেন ম্যাপের মধ্যেই, গ্লোব-এর গোল বলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। হঠাৎ নীল রঙে আঁকা সমুদ্র, ছোটো ছোটো অক্ষরে লেখা পৃথিবীর বিভিন্ন শহরগুলোর নাম আমার মতো এই সামান্য জনের জীবনেও সত্যি হয়ে উঠল। পৃথিবীটা এতদিনে ম্যাপ থেকে, গ্লোব থেকে ছাড়া পেয়ে আমার চেতনার মধ্যে, দৃষ্টির মধ্যে নড়ে-চড়ে উঠল জীবন্ত হয়ে। স্মৃতির মধ্যে এল।
হঠাৎ টবী বলল, রুদ্রদা, তুমি বলছ তাহলে আমি আইলীনের প্রতি অন্যায় করেছি?
পরক্ষণে নিজেই বলল, আসলে জানো, এখানে ভারতীয় সাধারণ ছাত্র যারা পড়তে আসে, বা চাকরি নিয়ে আসে, তাদের সঙ্গে যত মেয়েরই দেখা সাক্ষাৎ হয়, তাদের সঙ্গে ঠিক প্রেম বলতে আমরা দেশে যা বুঝি তেমন সম্পর্ক হয় না। তোমাকে কি বলব বুঝিয়ে বলতে পারছি না–সম্পর্কের বেশিটাই শরীরনির্ভর–অর্থনির্ভর।
তারপর বলল, সত্যিকারের প্রেম বলতে যা বোঝায় তা কি আজকাল আছে? দেশেও কি আছে? মনে হয় সমস্ত ব্যাপারটাই বদলে গেছে অনেক।
আমি বললাম, তুই কিন্তু যা বললি, তাতে আইলীন তোকে সত্যি সত্যি ভালোবেসেছিল। তোর কাছে তো তার প্রত্যাশার কিছু ছিল না।
কিছু না। কিছু না। টবী বলল।
তারপর বড়ো আরেক ঢোক বিয়ার গিলে বলল, আজ না হয় দু-পয়সার মুখ দেখেছি নিজের ফ্ল্যাট কিনেছি–গাড়ি চড়ছি–ভালো ভালো ক্লাবের মেম্বার হয়েছি, কিন্তু সেদিন? সেদিন আইলীন শুধু ভালোই বাসেনি আমাকে–অনেকরকম সাহায্যও করেছিল।
আমি বললাম, তুই পালিয়ে না এসে সুসানকে মিট করলে পারতিস। আইলীনের সব খবরাখবর পেতিস।
ও চোখ বড়ো করে বলল, স্মিতা জানে না যে।
জানলেও বা কী? আমি বললাম।
টবী আশ্চর্য চোখে আমার দিকে তাকাল।
তারপর বলল, আমার সন্দেহ হয় তুমি আদৌ লেখক কি না। মেয়েদের তুমি কিছুই বোঝোনি! তোমার ধারণা স্মিতা বুঝত কিছু? কিছুই সে বুঝত না। মেয়েরা, সে যে-দেশের মেয়েই হোক না কেন, কতগুলো ব্যাপার কখনো বোঝেনি। বুঝবেও না। যতই তুমি বোঝাতে যাও। বোঝাতে চাওয়াও মূর্খামি।
তারপর টবী অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, আইলীনের ব্যাপারটাকে আমি কখনো আমল দিইনি। নিজেকে নিজে চিরদিন জাস্টিফাই করে এসেছি। ভেবেছি, আই ওজ ওলওয়েজ রাইট। অ্যাণ্ড শী ওজ অলওয়েজ রং। তোমার কথায় এখন দেখছি ভেবে দেখতে হবে। অবশ্য করার কীই বা আছে এখন। ভাবনাই সার। কিন্তু দাদা-প্রেম-টেম এসব সুক্ষ্ম ব্যাপার সকলের জন্যে নয়। তোমরা লেখক-টেখক তোমাদের এসব মানায়–মানে তোমরা এসবের ফাইনারিজগুলো বোঝো–আমি ডাহা মিস্ত্রি–এঞ্জিনিয়র এল আর যাই এল–আমি এসব ঠিক বুঝিনি কখনো। ভুলটা আইলীনেরই। ও ভুল করে ভুল লোককে ভালোবেসেছিল। ওসব ভালোবাসা-টাসা আমার আসেনি। হিন্দুমতে বাবা-মায়ের দেখে দেওয়া মেয়ে বিয়ে করে নিয়ে এসেছি–বউ আমার বেঁচে থাক–সব সাদা চামড়ার মেয়ের মুখে ছাই।
টবীর কথার ভাষা ও রকম দেখে মনে হয় টবী একটু হাই হয়ে গেছে। অথচ ও এত সহজে হাই হওয়ার ছেলেই নয়। মানুষের মন বড়ো দুয়ে ব্যাপার। মনই বোধহয় শরীরকে চালায়। মন বেসামাল হলে শরীরের বেসামাল হতে দেরি সয় না।
আমি চুপ করে পথের দিকে চেয়েছিলাম। ওর পুরোনো দিনের ভুলে যাওয়া ও ভুলে-থাকা ভাবনাকে ফিরিয়ে আনার পেছনে আমার অপরাধ হয়তো কম নয়। কিন্তু মুখে ও আজ যাই বলুক, টবীর ভেতরেও যে একটা আশ্চর্য নরম মানুষ ছিল, যার খোঁজ দেশে কি বিদেশে কেউই রাখেনি, এই মানুষটাকে জানতে পারলাম আমি–এই-ই মস্ত লাভ।
ওইখানে বসে, চতুর্দিকের হই-হই, গাড়ির আওয়াজের মধ্যে আমার হঠাৎই মনে হল যে, সারাজীবন বড়ো কাছাকাছি থেকেও আমরা একে অন্যের বহিরঙ্গ দিকটাকেই জানি জানতে পাই–অন্তরঙ্গ রূপ তত সহজে প্রকাশিত হয় না–প্রকাশিত হলেও সেই রূপের দেখা পেতে দেবদুর্লভ ভাগ্যের দরকার হয়। তাই বহিরঙ্গকেই অন্তরঙ্গ বলে ভুল করতে করতে সেইটাই একমাত্র ও অমোঘ রূপ বলে বিশ্বাস জন্মে যায়। তখন ভেতরের গভীর জলের বাসিন্দা আসল মানুষটা কখনো বাইরে রোদ পোয়াতে এলে–তাকে রোদ পোয়ানো জল-ঢোঁড়া সাপের মতো আমরা ইট-পাটকেল মেরে উত্যক্ত করি। সঙ্গে সঙ্গে সে আবার ঝুপ করে জলে নেমে অদৃশ্য হয়ে যায়।
কতক্ষণ যে আমরা ওখানে বসেছিলাম, কতবার বিয়ার মাগ ভরতি করে এনেছিলাম মনে নেই। বেশ ঠাণ্ডা লাগছিল বাইরে হিমে বসে থেকে।
বললম, টবী, এবার চলো ওঠা যাক।
টবী আমার দিকে তাকাল। কথা বলল না।
অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, চলো রুদ্রদা! তোমাকে আইলীনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। ইউ উইল লাইক হার। ভেরি নাইস গার্ল ইনডিড। ও কাছেই থাকে।
আমি বললাম, টবী, বাড়ি চলল।
টবী বলল, নো। নট ন্যাউ।
তারপর বলল, তুমি একটা ক্যাব নিয়ে চলে যাও রুদ্রদা। আইলীনের সঙ্গে অনেক কথা জমে আছে। ও যদি বাড়ি থাকে, তাহলে হাঁটু গেড়ে বসে ক্ষমা চাইব ওর কাছে।
টবী কোনো কথা না শুনে আমাকে বলল, তুমি এগোও। আমি আইলীনের বাড়ি ঘুরে যাচ্ছি।
কোটের কলার তুলে বেজওয়াটার স্ট্রিট ধরে হাঁটতে হাঁটতে এগোচ্ছিলাম। ঝুরুঝুরু করে হাওয়া দিয়েছে একটা। আর দিনকয়েক পরই ফল শুরু হবে। প্রায় এক কিলোমিটার গিয়ে একটা ক্যাব পেলাম।
বাড়ি পৌঁছেছি, দেখি টবীও ওর গাড়ি পার্ক করছে।
গাড়ি লক করে টবী এগিয়ে এল।
আমি কথা না বলে ওর দিকে তাকালাম।
টবী বলল, আইলীন ও ঠিকানায় নেই। বহুদিন হল চলে গেছে।
মনে মনে আমি খুশি হলুম। খুশি হলাম আইলীনের জন্যে এবং টবীর জন্যেও। মুখে। কিছুই বললাম না।
লিফটের দরজা খুলে ধরলাম টবীর জন্যে।
.
০৪.
আমরা টবীর খাওয়ার ঘরে বসে প্রাতরাশ খাচ্ছিলাম। প্রাতরাশ খাওয়ার পরই টবী ও স্মিতা দুজনেই আমাকে ভিক্টোরিয়া স্টেশানে ছাড়তে যাবে। সেখান থেকে কসমস ট্যুরস-এর ট্যুর নিয়ে আমি কন্টিনেন্টে যাব। বারো দিনের জন্যে।
বেশ রোদ উঠেছে আজ। টবীদের বাড়ির নীচে যেখানে গাড়িগুলো পার্ক করানো থাকে সেখানে ও বাগানে বাচ্চারা খেলছে দৌড়াদৌড়ি করে। তাদের গলার চিকন স্বর কাঁচের বন্ধ জানালা পেরিয়েও ওপরে আসছে। টবীর প্রতিবেশী মিস রবসন জিনের বেল-বটস-এর ওপরে রংচটা চামড়ার জার্কিন চাপিয়ে পাইপ ও ব্রাশ দিয়ে গাড়ি ধুচ্ছেন।
আজ শনিবার। অফিস ছুটি। সকলের কিন্তু বড়ো কাজের দিন আজ। স্মিতার আজ ওয়াশিং ডে। আমাকে ছেড়ে দিয়ে এসে কাপড় কাঁচবে–যদিও ওয়াশিং মেশিনে–তারপর চুল শ্যাম্পু করবে–আমাকে ছেড়ে দিয়ে ফিরে আসার সময়ে সপ্তাহের বাজার করে আসবে ডিপার্টমেন্টাল স্টোরস থেকে।
কফির পেয়ালা এগিয়ে দিতে দিতে স্মিতা বলল, ভাসুরঠাকুর, তুমি চলে গেলে বড়ো ফাঁকা ফাঁকা লাগবে কয়েকদিন।
আমি হেসে বললাম, কয়েকদিনমাত্র। পৃথিবী ছেড়ে কেউ গেলেও কয়েকদিনই ফাঁকা ফাঁকা লাগবে। তারপর সব ঠিক হয়ে যায়। তারপর বললাম, তোমাকে থ্যাঙ্ক ইউ জানাই। তুমিই আমাকে লানডানে সাবালক করেছ, টিউবে চড়তে শিখিয়েছ; ককনী ইংরিজি শিখিয়েছ।
টবী বলল, শেখাবার চেষ্টা করেছে এল।
যাই-ই হোক, আমি বললাম।
আমার স্যুটকেসটা হাতে নিয়ে টবী এগোল। পেছনে পেছনে আমি আমার নতুন কেনা ওভারকোট-টুপি ইত্যাদি নিয়ে। স্মিতা সবচেয়ে শেষে ঘর বন্ধ করে লিফটে এসে ঢুকল।
কেউ আমরা কোনো কথা বললাম না। এই কয়েকদিনের কারণ-আকারণের হাসি গল্প খুনসুটির সমস্ত উচ্ছ্বাস লিফটের মধ্যে কাছাকাছি ঘোঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে থাকা আমাদের বুকের মধ্যে এক স্তব্ধ নীরবতায় জমে গেল।
একতলায় নেমে লিফটের দরজা খুলে টবী বলল, কী হল স্মিতা–এত চুপচাপ কেন? রুদ্রদা তো বারোদিন পরই আবার আসছে ক্যানাডা যাবার পথে।
স্মিতা হাসল। বলল, তুমিও তো চুপচাপ।
ভিক্টোরিয়া ট্রেন টার্মিনাসে যখন এসে পৌঁছোলাম তখন দেখি স্টেশনের একটা বিশেষ জায়গা ভিড়ে-ভিড়াক্কার। বাহুতে ব্যাজ লাগানো কসমস-ট্রস-এর কর্মচারীরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমাদের দেশে খাজনার চেয়ে বাজনা বেশি। যত যাত্রী বিভিন্ন ট্যুরে যাচ্ছে, আজ আমাদের দেশ হলে কর্মচারীর সংখ্যা অসংখ্য হত। যাই-ই হোক, খুঁজে-পেতে আমার যে ট্যুর সেই ট্যুরের কর্মচারীটিকে পাওয়া যেতেই তাকে দেখে আমি যেমন পুলকিত হলাম সেও আমাকে দেখে তেমনই পুলকিত হল। কারণ ট্রেন ছাড়ার আর বেশি দেরি ছিল না। যা বোঝা গেল তা হচ্ছে কসমস কোম্পানির বিভিন্ন ট্যুরের জন্যে লানডান থেকে ডোভারের এই বিশেষ ট্রেনটির বন্দোবস্ত হয়েছে। ট্রেনের প্রায় সব যাত্রীই বিভিন্ন ট্যুরের যাত্রী।
টবী আমার সময়াভাবের জন্যে যে বারোদিনের ট্যুরের টিকিট কেটেছিল–তাতে লেখা ছিল আটটি দেশ এবং প্যারিস। অর্থাৎ যেন প্যারিসের আকর্ষণ অন্য একটি পুরো দেশেরই মতো। এই ট্যুর একেবারেই জনতা ট্যুর। যাদের অবস্থা ভালো তারা কোন দুঃখে এই অধমের সঙ্গে যাবে। কসমস কোম্পানি অবশ্য দামি ও বিলাসবহুল ট্যুরের ব্যবস্থাও করেন।
দেখতে দেখতে ট্রেন এসে গেল। সকলের সিটই রিজার্ভ করা আছে। যে-যার জায়গায় গিয়ে বসলাম।
টবী ও স্মিতাকে ট্রেন-ছাড়া অবধি অপেক্ষা করতে বারণ করলাম। ওদের অনেক কাজ ছিল। এই উটকো দাদা এসে পড়ে তো এদের সময়ের এবং টাকা পয়সার শ্রাদ্ধ ছাড়া আর কিছুই করিনি।
ওরা চলে গেলে আমি ওভারকোট ও টুপি সামলেসুমলে রেখে নিজের সিটে বসলাম। শীতের দেশের লোকরা যে কী সপ্রতিভ অবলীলায় ওভারকোট টুপি ছাতা ছড়ি সব সামলায় তা দেখলে সত্যিই অবাক হতে হয়।
বসে পড়ে মনে হল এই-ই প্রথম আমার একা একা বিদেশ যাত্রা শুরু হল। বোম্বে থেকে প্লেনে ফ্রাঙ্কফার্ট হয়ে লানডানে আসা ইস্তক তো টবী ও স্মিতাই খবরদারি করেছে। এবার থেকে রীতিমতো স্বাবলম্বী। আট-আটটা দেশ ঘুরতে হবে–কতবার যে পাসপোর্ট বের করতে হবে–বিভিন্ন দেশের ভিসা দেখাতে হবে–কতবার যে কত জায়গায় নিজের নাম জন্ম তারিখ পাসপোর্টের নম্বর লিখতে হবে তা জানা ছিল না। ডোভারে গিয়ে আমরা জাহাজে করে বেলজিয়ামের অস্টেণ্ডে গিয়ে নামব। অস্টেণ্ডে কসমস কোম্পানির বাস দাঁড়িয়ে থাকবে। ওই বাসে করেই আমাদের বারো দিনের ট্যুর। রাতে শুধু বিভিন্ন জায়গায় হোটেলে রাত্রিবাস। আর সারাদিন চলা।
আমার পাশে একজন অত্যন্ত লম্বা প্রৌঢ়া মহিলা–উটপাখির মতো খোলা জানলার কাঁচের মধ্যে দিয়ে গলা বার করে একটি যুবক এবং এক কিশোরীর সঙ্গে অনর্গল কথা বলে যাচ্ছিলেন। তাঁর কথা শুনতে শুনতে আমার কেবলই মনে হচ্ছিল যে, ইংরেজ পুরুষরা কথা কম বললেও মহিলারা অত্যন্ত বেশি কথা বলেন। এবং সব দেশেই এক ধরনের বেশি বয়েসি অথচ নেকুপুযুমুনু মহিলারা প্রচুর জ্বালান অন্যদের।
কথাবার্তায় বোঝা গেল যে ভদ্রমহিলা অবিবাহিতা। যুবকটি তাঁর ভাইপো এবং কিশোরী নাতনি।
ট্রেন ছেড়ে দিলে ভাবলাম বাঁচা গেল। কিন্তু পরক্ষণেই বুঝলাম যে কত বড়ো ভুল। ভাইপো ও নাতনি চলে গেলে তিনি আমাকে নিয়ে পড়লেন।
এদিকে ট্রেন চলেছে ইংলিশ গ্রামের মধ্যে দিয়ে। দেখতে দেখতে আমরা ক্যান্টারবেরি এসে পৌঁছেছিলাম। রবিনহুড কি এই জায়গায় জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতেন? শার্লক হোমস-এর কত কান্ডকারখানা আছে এসব অঞ্চল নিয়ে। ক্যান্টারবেরির গল্প পড়েনি এমন শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্ত কোথায়?
সাধারণত মেয়েদের মধ্যে ন্যাকামি আমার অপছন্দ নয়। ন্যাকামিটা মেয়েদের চেহারা ও চরিত্রের সঙ্গে যেমন ওতপ্রোতভাবে মানায় তাতে নারীত্বের একটা বিশেষ নরম দিক প্রকাশিত হয় বলেই আমার বিশ্বাস। কিন্তু এই বিগতযৌবনা মহিলার বসার ধরন, কথা বলার কায়দা, চোখ ঘোরাবার ধরন-ধারণ দেখে ইচ্ছে হল যে ডোভারে নেমেই ওঁকে একটা বড়ো আয়না কিনে প্রেজেন্ট করি।
চারপাশে যারা বসেছিল সকলকে দেখা যাচ্ছিল না। যাদের দেখা যাচ্ছিল তাদের কারও সঙ্গেই আলাপ ছিল না। পরে এদের সকলের সঙ্গেই কত ঘনিষ্ঠতা হবে–একসঙ্গে খাওয়া বসা-হাঁটা-চলা। কনডাকটেড ট্যুরে এইটেই মস্ত লাভ যে বহুদেশের বহুলোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেশার সুযোগ পাওয়া যায়।
দেখতে দেখতে ডোভারে এসে দাঁড়াল ট্রেন। একটি সুন্দরী অল্পবয়েসি বেলজিয়ান মেয়ে –কসমসের গাইড আমাদের বলে গেল যে তোমাদের স্যুটকেস নিয়ে কাস্টমস-এর হাত পেরিয়ে এক জায়গায় রেখে দিয়ে। আমরা বোটে নিয়ে যাব এবং বার্থে পাঠিয়ে দেব।
যেহেতু বোট বেলিজয়ামে যাচ্ছে এবং আমরা বোটের যাত্রী–ডোভার স্টেশানেই ব্রিটিশ কাস্টমস আমাদের পাসপোর্ট-টাসপোর্ট দেখে–এনিথিং টু ডিক্লেয়ার? বলে জিজ্ঞাসাবাদ করে ছেড়ে দিল।
আমরা বোট মানে নৌকো বুঝি। নৌকোর চেয়ে বড়ো মোটর-লঞ্চ তারপর স্টিমার তারপরে জাহাজ–শিপ। কিন্তু এখন সারাপৃথিবীতে বোট মানে জাহাজ। ভাষা নিয়ে অনেক রমদা-রমদি হয়েছে ইদানীং। ভাষাতত্ত্ববিদদের হাতপাখার ডাঁটি দিয়ে বসে বসে পিঠের ঘামাচি মারতে হয় দেখে পুরোনো ভাষা ও উচ্চারণ পালটে দিয়ে তাঁরা নিজেদের অস্তিত্ব জাহির করছেন। ধরা যাক ইংরিজি Schedule কথাটা। আমরা জানি শিডিউল। কেউ কেউ বলেন শেডল। কিন্তু আমেরিকানদের দৌলতে ইংরিজি ভাষাটাই গায়েব হতে বসেছে। Schedule-এর বর্তমান উচ্চারণ পুরো পশ্চিমজগতে এখন কেজুল। পুরোনো ইংরিজি কথাটাকে এমন ডাক্তারি বানানের কায়দায় উচ্চারণ করে কী উপকার হল জানি না কিন্তু এখন ওখানে শিডিউল বললে কেউ বুঝবে না।
ব্রিটিশ কাস্টমস-এর কালো ব্লেজার-পরা গুঁফো অফিসারদের চকচকে জুতোর চাকচিক্যের দিকে শেষবার চেয়ে প্রকান্ড জাহাজের হাঁ-করা পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে গেলাম। সমস্ত পশ্চিমি দেশে যা সত্যিই আশ্চর্য করে তা সকলের সৌজন্য। যে লোক টিকিট কেটে ট্রেনে চড়েছে, যে দোকানে এসেছে, যে-আয়কর দিচ্ছে তারা সকলেই ভি-আই-পি। সৌজন্যে কিছুমাত্র খরচ হয় না কিন্তু বিনিময়ে যা পাওয়া যায় তার তুলনা নেই। সবচেয়ে বড়ো কথা যে সৌজন্যে বিশ্বাস করে সে অন্যের প্রতি তা দেখিয়ে নিজেকেই এক উন্নত আসনে অধিষ্ঠিত করে। সৌজন্যে যা পাওয়া যায় এ জীবনে তা অন্য কোনো কিছুতেই পাওয়া যায় না।
বোটে উঠে একটা বসার জায়গা ঠিক করে মালপত্র তাতে রেখে সামনের ডেকে এলাম। হু-হু করে কনকনে হাওয়া আসছে ইংলিশ চ্যানেলের ওপর দিয়ে। ওভারকোট ও টুপি পরেও জমে যাচ্ছি। অথচ ওদেশে তখনও সামার। ঝকঝক করছে রোদ কিন্তু মনে হচ্ছে সোনালি বরফ পড়ছে আকাশ থেকে।
পাশেই ডোভারের বিখ্যাত হোয়াইট রকস। দেখা যাচ্ছে। ডোভারকে বলে ডোভার অফ দ্য হোয়াইট রকস। সাদা সী-গালের ঝাঁক উড়ছে নীল জলের ওপর। সাদা পাহাড়গুলোর ওপরে পাখিগুলোউড়ে বসছে। পাহাড়ের খাড়া গায়ের ফাঁক-ফোকরে সী-গালেদের বাসা।
নীচে ডিউটি-ফ্রি শপ খুলে দিয়েছে। হুইস্কি, চকোলেট আর পারফিউম কেনার ধুম পড়ে গেছে। রথযাত্রার মেলায় তালপাতার বাঁশি কেনা গরিব ছেলের মতো আমি গিয়ে গুটি গুটি একটিন পাইপের তামাক কিনে ফিরে এলাম।
এবার বোট ছাড়ল। আজ সমুদ্র বড়ো অশান্ত। টবী ও স্মিতা বলে দিয়েছিল যে জাহাজে উঠে কিছু খেয়ে নিয়ে নইলে সী-সিক হয়ে পড়বে। ডাইনিং রুম দুটো। একটাতে ওয়েটার খাবার সার্ভ করে। সেখানে দাম বেশি। আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়। অন্যটাতে সেলফ সার্ভিস। এককাপ কফি ও দুটো স্যাণ্ডউইচ দিয়ে লাঞ্চ-পর্ব সমাধা করলাম।
আমার সিটের পাশে একটি অল্পবয়েসি ইংলিশ ছেলে বসেছিল। ও ব্রাসেলস-এর কলেজে পড়ে ইংরিজি এবং তুলনামূলক সাহিত্য। ও বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়কে চেনে না কিন্তু সত্যজিৎ রায়কে চেনে। সারাপৃথিবীতে রসিক সকলে অপু-ট্রিলজি দেখেছে কিন্তু পথের পাঁচালির লেখক যে সম্মানের লোক তা জানে না। একথা জেনে দুঃখ হল। ছেলেটির সঙ্গে অনেক্ষণ গল্প করে কাটানো গেল। আজকাল পৃথিবীর প্রায় সব জায়গাতেই পড়াশোনা একটা ভালো চাকরির সিঁড়ি। পড়াশোনা করার আনন্দে খুব কম ছেলে মেয়েই পড়াশোনা করে আজকাল। কেন জানি না!
বোট বড়ো ঝাঁকাচ্ছে। একদল মেয়ে বমি-টমি করে অস্থির। লেডিজ রুমের সামনে যেন কাঙালি-ভোজন লেগে গেছে। কেউ মেঝেতে পা ছড়িয়ে বসে কেউ দেওয়ালে মাথা ঠেকিয়ে চোখ বন্ধ করে অসহায় আধশোয়া ভঙ্গিতে বসে আছে।
মেমসাহেব মানে মার্কেন্টাইল ফার্মের বড়োসাহেবের দারুণ দারুণ গাউন পরা সুগন্ধি পারফিউম মাখা মেয়েছেলে বলেই জানতাম। মেমসায়েবদেরও এমন হেনস্থা হয় তা নিজে চোখে দেখে মনে মনে একটু খুশি হলাম। আসলে ব্যাটা-ছাওয়া; ব্যাটা-ছাওয়া; বিটি ছাওয়া; বিটি-ছাওয়া। পোশাক যার যাই-ই হোক না কেন–আর গায়ের রং যাই-ই হোক।
বিকেল হয়ে এসেছে। রোদে মাতাল হয়ে ওঠা উথাল-পাথাল করা চ্যানেলের ঢেউ-এর মাথায় ফেনা চিকমিক করে উঠছে। দূরে ড্যাঙা দেখা যাচ্ছে। আমরা বেলজিয়ামের তীরে এসে গেছি বলে মনে হচ্ছে। অস্টেণ্ডের জেটির দিকে মুখ করল বোট। ধীরে ধীরে দূরত্ব কমে আসছে। আবছা তীর স্পষ্ট হয়ে উঠছে। বন্দরে দাঁড়িয়ে থাকা আরও অনেক জাহাজের মাস্তুল-টাস্তুল দেখা যাচ্ছে।
কথা আছে জাহাজ থেকে নেমে বেলজিয়াম কাস্টমস ক্লিয়ার করে আমরা আমাদের বাসে উঠব। তারপর বাসে করে বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলস-এ পৌঁছোব। এ রাতটা ব্রাসেলস এই কাটাব। তার পরদিন ভোরে আবার বোরোব।
বোটে বমি না হলেও ওইরকম দোলানিতে শরীর খারাপ লাগছিল। একটা গা-গুলোনো ভাব। জাহাজ বন্দরে ভিড়তেই বোটের পেটের দরজা খুলে গেল। বাইরে থেকে কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া আসতে লাগল ভেতরে। হাওয়াতে শরীরটা চাঙ্গা হয়ে উঠল। এতক্ষণ হিটেড বোট থেকে বাইরের ঠাণ্ডা সম্বন্ধে কিছুই বোঝা যায়নি। বন্দরে নেমে মনে হল ঠাণ্ডা তো নয় যেন হাঙর-জুতোর মধ্যে ঢুকে পড়ে গোড়ালি কামড়ে ধরেছে।
মালপত্র হাতে নিয়ে সকলের সঙ্গে গুটিগুটি পা-পা করে বাইরে বেরোলাম। এত লোক ঘেঁষাঘেষি ঠেসাঠেসি কিন্তু হুড়োহুড়ি নেই, চেঁচামেচি নেই–আমাদের মতো এত বেশি অপ্রয়োজনীয় কথা বলে না পশ্চিমিরা–কথা বললেও ফিসফিস করে যাকে বলছে তাকে শোনাবার জন্যেই বলে–চারদিকের লোককে শোনাবার জন্যে বলে না।
হাতের মালপত্র নিয়ে জেটি থেকে নেমে এগিয়ে যেতেই দেখি সার সার বাস দাঁড়িয়ে আছে। প্রত্যেক বাসের সামনের উইণ্ডস্ক্রিনের ওপরে হলুদ কাগজে লেখা আছে কসমস কোম্পানির বিভিন্ন ট্যুরের নম্বর। আমাদের ট্যুরের নম্বর দুটো কুড়ি।
একটি মেয়ে হলুদ ব্যাজ বাহুতে লাগিয়ে প্রত্যেককে ট্যুর নম্বর জিজ্ঞেস করে করে যার যার বাসের দিকে পাঠিয়ে দিচ্ছে।
একটি চব্বিশ-পঁচিশ বছরের ইংলিশ ছেলে–পরনে একটা কালচে কড়ু ঝুঁয়ের ট্রাউজার, গায়ে কালচে গরম কোট-ঘাড়-অবধি নেমে আসা লালচে চুল নিয়ে দাঁড়িয়ে টিকিট দেখে দেখে কার কোথায় বসার জায়গা বলে দিচ্ছে।
এগিয়ে গিয়ে নিজের জায়গায় গিয়ে বসলাম। জানলার পাশের সিট আমার। লক্ষ করে দেখলাম ট্যুরের বেশির ভাগ লোকই বয়স্ক। অল্পবয়েসি কিছু ছেলে-মেয়েও ছিল। কার কী জাত, কে কোন লোক জানি না। আমার পাশে কার সিট তাও জানি না। এক-একজন করে বাসের পাদানিতে উঠে আসছে আর তার দিকে তাকাচ্ছি। শেষে আমার যেমন বরাত তেমনই ঘটল। একজন গোলাকৃতি ফিলিপিনো মহিলা আমার পাশে এসে বসলেন। একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল অজানিতে। ইনি না হয়ে যে-কোনো একজন অস্ট্রেলিয়ান বা ইজরায়েলি তরুণীও তো আমার বারোদিনের গা-ঘেঁষা সঙ্গিনী হাত পারত!
যাই-ই হোক তৎক্ষণাৎ আলাপ করে ফেললাম। জানা গেল তিনি একজন গাইনিকোলজিস্ট –ফিলিপিনস থেকে বৃত্তি নিয়ে ইংল্যাণ্ডে এসেছেন উচ্চতর শিক্ষার জন্যে। এই ট্যুর নিয়েছেন দেশ দেখবার জন্যে–বৃত্তির টাকা জমিয়ে। বৃত্তি ছাড়াও ভালো চাকরি করেন তিনি। এবং একটু কথা বলেই বোঝা গেল ভদ্রমহিলা অত্যন্ত যোগা। আপাতযোগ্যতা ও তাঁর বিশেষশিক্ষা প্রয়োগ করতে পারেন এমন কোনো সম্ভাবনা এই বিরাট বাসের প্রায় জনা চল্লিশকে যাত্রীকে পুঙ্খানুপুঙ্খ করে দেখেও মনে হল না। গাইনিকোলজিস্ট না থেকে আমাদের বাসে কোনো জেনারাল ফিজিশিয়ান বা হার্ট স্পেশ্যালিস্ট থাকলে বোধহয় ভালো হত।
বাসের দু-পাশে পেটের তলায় হোল্ড আছে। সেখানে আমরা আমাদের মালপত্র শনাক্ত করার পরেই সেই ইংলিশ ছেলেটি এবং বেঁটে-খাটো শক্তসমর্থ চেহারার বয়স্ক একজন শ্বেতাঙ্গ লোক সেগুলোকেহোল্ডে তুলে দিলেন। সেই-ই প্রথমবার। তারপর সমস্ত পুরুষদের নিজের নিজের মাল ছাড়াও সমস্ত মহিলাদের মাল চাঁদা করে বইতে হয়েছে এবং বার বার তুলতে-ওঠাতে হয়েছে। এটা একটা বড়ো শিক্ষা। টাকা দিয়ে টিকিট কেটে বেড়াচ্ছি বলেই যে মহারাজা হয়ে গেছে কেউ একথা বিশ্বাস করা ইংরেজদের স্বভাবে নেই। মেয়েদের ওরা যা সম্মান করে ও মেয়েদের যেমন তুলো-তুলো করে রাখে তা বলার নয়। যে-কোনো দেশের সমাজে মেয়েদের আসন কোথায় তা দেখে সেই জাতের সাংস্কৃতিক উচ্চতা বা নীচতা বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না।
দেখতে দেখতে সব প্যাসেঞ্জার এসে গেলেন। বাসের প্রতিটি সিট ভরে গেল। তখন সেই ইংলিশ ছেলেটি বাসের সামনে তার ছোটো আসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বাসের ভেতরের যোগাযোগের অ্যামপ্লিফায়ারের মাউথপিস তুলে নিয়ে বলল, আমার নাম অ্যালাস্টার। আমি তোমাদের গাইড। পরের বারোদিন আমি সবসময় তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকব। তারপর স্টিয়ারিং-এ বসে থাকা সেই বেঁটে-খাটো শক্তসমর্থ ভদ্রলোকটিকে দেখিয়ে, যিনি মাল তুলতে অ্যালাস্টারকে সাহায্য করছিলেন–বলল, এঁর নাম জ্যাক। ইনি এই বাস চালাবেন। কসমস ট্যুরস লিমিটেডের পক্ষ থেকে এবং আমাদের দুজনের পক্ষ থেকে আমরা আপনাদের সকলকে এবং প্রত্যেককে স্বাগত জানাচ্ছি। আশা করি পরের বারো দিন আপনাদের ভালোই কাটবে।
বাসটা ছেড়ে ছিল। আমরা বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলস-এর দিকে এগিয়ে চললাম।
অ্যালাস্টার বলল, আমরা ডিনার-টাইমে অর্থাৎ সাতটার সময়ে ব্রাসেলস-এর হোটেলে পৌঁছে যাব।
আমাদের প্রকান্ড বাসটা ভারি চমৎকার। অতখানি চওড়া বাসটার সমস্ত সামনেটা জুড়ে কাঁচ–অর্থাৎ বাসের যেখানে খুশি বসে সামনে পরিষ্কার দেখা যায় ড্রাইভার ও গাইডের সিট নীচুতে। প্যাসেঞ্জাররা যেখানে বসেন সে জায়গাটা অপেক্ষাকৃত উঁচু। দু-পাশে দু-সারি সিট। পাশাপাশি দুজন করে বসার। বাসটা ওয়েস্ট জার্মানির তৈরি। নাম Sentra-240 সি. সি.। একলিটার ডিজেলে চার কিলোমিটার করে যায়। প্যাসেঞ্জারদের সিটগুলো এরোপ্লেনের সিটের মতো আরামের। বাসের পেছনে ব্লোয়ার আছে। গরম হাওয়া পায়ের পাশ দিয়ে নলে করে বইয়ে দেওয়া হয়–যাতে ভেতরটা গরম থাকে।
দেখতে দেখতে আমরা হাইওয়েতে এসে পৌঁছোলাম। তারপর হু-হু করে ছুটল বাস। অ্যালাস্টার মাইক্রোফোনে বিবরণী দিয়ে আমাদের ডানদিক বাঁ-দিকের দ্রষ্টব্য জিনিস দেখাতে দেখাতে যাচ্ছিল।
সন্ধ্যার বাতি জ্বলে উঠল। আমরা এসে ব্রাসেলস-এ পৌঁছোলাম। বাস থেকে বার বার স্যুটকেস ও মাল নামিয়ে বয়ে নিয়ে আসতে হল হোটেলের রিসেপশানে। অ্যালাস্টার ও রিসেপশনিস্ট নাম ডেকে ডেকে যার যার ঘরের চাবি তাকে তাকে দিয়ে দিল। ওই হোটেলে লিফট ছিল। মাল সিঁড়ি দিয়ে বইতে হল না সে যাত্রা। পরে অনেকানেক হোটেলে পাঁচ-ছ তলা অবধি নিজের স্যুটকেস বয়ে উঠতে হয়েছিল।
ঘরে এসে হাত মুখ ধুয়ে ডাইনিং রুমে আসতে হল ডিনার সারার জন্যে। স্যুপ, বিফ স্টেক ও পুডিং। তারপর নাইট-ট্যুরে বেরোনো গেল। নাইট-ট্যুরে অ্যালাস্টারের ছুটি। অন্য একটা বাসে করে আমরা গেলাম। ড্রাইভারই গাইড। একহাতে স্টিয়ারিং ধরে অন্য হাতে কমুনিকেশন সিস্টেমের মাউথপিস ধরে রাতের ব্রাসেলস দেখাতে দেখাতে চলেছে।
ব্রাসেলস-এর দ্রষ্টব্যর মধ্যে অন্যতম প্রধান হচ্ছে Atomieum এখানে ওয়ার্লড ফেয়ারের সময়ে এটা তৈরি হয়েছিল। স্ট্রাকচারাল এঞ্জিনিয়ারিং-এর দক্ষতার পরাকাষ্ঠা। অনেকগুলো বিভিন্নাকৃতি বড়ো ছোটো অতিকায় বল যেন সাজানো আছে। উচ্চতাতে গড়ের মাঠের মনুমেন্টের চেয়েও উঁচু। লিফট আছে ওপরে উঠবার। নীচের দিকের বলগুলোতে নানারকম রেস্তোরাঁ। সবচেয়ে ওপরের বলটার মধ্যে যে রেস্তোরাঁ সেটা খুব এক্সপেনসিভ। আমাদের মতো কসমস ট্যুরের প্যাসেঞ্জারের সাধ্যের একেবারেই বাইরে। তবু দেখেই চক্ষু সার্থক করলাম দূর থেকে।
একটা ম্যাল মতো জায়গায় বাস দাঁড়াল। ড্রাইভার-কাম-গাইড বলল–সকলে ডান দিকে দেখুন। তাকিয়ে দেখি একটা ব্রোঞ্জের তৈরি বাচ্চা ছেলের মূর্তি। ছেলেটি বাঁ-হাতে প্রত্যঙ্গ বিশেষ ধরে হিসি করছে। গাইড বলল, লক্ষ করুন ওর ডান হাত ফ্রি আছে যাতে সুন্দরী মহিলা দেখলেই স্যালুট করতে পারে।
আমাদের দেশ হলে এমা! কী অসভ্য ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক রব উঠত। কিন্তু দেখলাম ব্যাপারটার রসিকতা সকলেই পুরুষ ও নারী নির্বিশেষে দারুণ উপভোগ করল। পরে দেখেছিলাম শুধু বেলজিয়ামেরই সর্বত্রই নয়–পৃথিবীর অন্যান্য অনেকানেক জায়গায় এই পিসিং বয়ের মূর্তি একটা খুব ফেভারিট স্যুভেনির। এই ছেলেটি নানাজনের কাছ থেকে নানারকম জমকালো পোশাক পায়। সেসব পোশাক সে নাকি তার জন্মদিনে পরে। তার সঠিক জন্মদিন নিয়ে নাকি বিতর্কের অবকাশ আছে, কিন্তু পোশাকের কোনো অভাব নেই বলে সে সব-দিনই ভালো ভালো পোশাক পরে। স্যার মরিস শিভলিয়র নাকি তাকে জব্বর একটি পোশাক দিয়েছিলেন।
এরপর বাস এসে দাঁড়াল বেলজিয়ামের রাজার রাজবাড়ির সামনে। এই রাজবাড়িতে বসে নেপোলিয়ান তাঁর রাশিয়া আক্রমণের প্ল্যান করেছিলেন।
তারপর আরও অনেক কিছু দেখা-টেখার পর গাইড বলল, এবার আপনাদের একটা আশ্চর্য জিনিস দেখাব। মহিলাদের বলল, স্বামীদের সাবধানে রাখবেন যাতে পরে এইখানে আবার ফিরে না আসেন। অবাক কান্ডই বটে! একটা সরু গলিতে বাস ঢুকল। দেখি দু পাশের বাড়িগুলোর একতলা এবং দোতলাতে কাঁচের শো-উইণ্ডো। অনেকটা শো-কেশের মতো। সেই এক-একটা চৌকো কাঁচের বাক্সের মধ্যে এক-একজন করে নগ্না রমণী বসে বা দাঁড়িয়ে আছেন। এ রসে যারা রসিক তারা যার যার পছন্দ অনুযায়ী বেছে নেবে।
বেলজিয়ামের কোনো নিজস্ব ভাষা নেই। এখানকার ভাষা ডাচ অথবা স্প্যানিশ। দুটো ভাষাই চলে কিন্তু ডাচ ভাষায় কথা বলে একান্ন শতাংশ লোক আর স্প্যানিশ ভাষায় ঊনপঞ্চাশ শতাংশ লোক।
বাসটা হোটেলের দিকে ঘুরল। ব্রাসেলস থেকে Antwerp বিখ্যাত বন্দর মাত্র পঁচিশ মাইল। তারপর রাত প্রায় এগারোটার সময়ে আমাদের ছোটো কিন্তু সুন্দর হোটেলে আমরা ফিরে এলাম। হোটেলের নাম A.B.C. Hotel.
দেশ ছেড়ে এসে–লানডানের ভায়ার বাড়ির আতিথ্যের পর এই প্রথম রাত বাইরে কাটানো। হাত-মুখ ধুয়ে ঘরের বাতি নিবিয়ে শুয়ে পড়লাম। পালকের গদি, পালকের লেপ, পালকের বালিশ। ভারি আরাম। শরীরে খুব ক্লান্তি কিন্তু দেশ বেড়ানোর আনন্দ ও উত্তেজনা মিশে থাকায় ঘুম আসছিল না। তার ওপর অ্যালাস্টার বলে দিয়েছিল যে, ভোর পাঁচটায় উঠতে হবে। সাড়ে পাঁচটায় ব্রেকফাস্ট খেতে হবে নিজের নিজের মাল নিয়ে এসে। ঠিক ছ টায় বাস ছেড়ে দেবে। এই ঠাণ্ডাতে অত সকালে উঠতে হবে শুনেই ভয়ে ঘুম আসছিল না। বিছানা ছেড়ে এসে একবার কাঁচের জানালার সামনে দাঁড়ালাম। রাতের ব্রাসেলস-এর আলো ঝলমল করছে। আমার ঘরের মধ্যে অন্ধকার। ভারি ভালো লাগছিল। কাল ভোরে আমরা ব্রাসেলস ছেড়ে লাকসেমবার্গ, গসবাগ হয়ে পশ্চিম জার্মানির বিখ্যাত ব্ল্যাক ফরেস্টের মধ্যে দিয়ে গিয়ে Denzlingen-এ গিয়ে রাত কাটাব।
অনেকক্ষণ জানলার সামনে দাঁড়িয়ে থাকার পর এসে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। শুয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমে চোখ ছেয়ে এল।
কে যেন দরজায় ধাক্কা দিয়ে ঘুম ভাঙিয়ে গেল।
ঘুম তার আগেই ভেঙে গেছিল। অত ভোরে উঠতে হবে এবং যদি ঘুম না ভাঙে এই আতঙ্কেই সারারাত ঘুম হল না। যতটুকু হল তা ছেঁড়া-ঘেঁড়া পাতলা ঘুম।
ঘরের মধ্যেই একটা বেসিন ছিল। মুখে-চোখে জল-টলও দেওয়া গেল। কিন্তু বাথরুমে যাওয়া এক সমস্যা। এক-এক তলায় দুটি করে বাথরুম। সেই তলায় যতজন লোক সকলের সেই বাথরুম দুটি ব্যবহার করতে হবে। অন্য লোকের প্রতি কনসিডারেশন ও পাছে দেরি হয়ে যায় এই ভয়ে বাথরুমে যাওয়া আর না-যাওয়া সমান।
স্যুটকেস গুছিয়ে নিয়ে, দাড়ি-টাড়ি কামিয়ে নীচে ব্রেকফাস্ট করতে নামা গেল।
ইংরেজরা আমাদের প্রভু ছিল বলে ব্রেকফাস্ট ব্যাপারটা আমাদের শেখা তাদের কাছ থেকে। ফুটজুস, পরিজ বা কর্নফ্লেকস, তারপর টোস্ট ডিম ইত্যাদি ইত্যাদি, সঙ্গে হয়তো চিকেন লিভার বেকন অথবা অন্য কিছু। কিন্তু কন্টিনেন্টাল ব্রেকফাস্ট বলতে যা বোঝায় তা হল গরম গরম ব্রেডরোলস–সঙ্গে টেবিলে-রাখা মাখন ও মার্মালেড–তারপর চা অথবা কফি-ব্যস।
যেমন ঠিক ছিল তেমনই সকলে সময়মতো তৈরি হয়ে বাসের কাছে আসা হল। বাস দাঁড়িয়ে ছিল একতলায় ডাইনিং রুমের একেবারে সামনে। তারপরই যতটুকু ব্রেকফাস্ট খাওয়া হয়েছিল তা হজম হয়ে গেল মহিলাদের স্যুটকেস হোল্ডে তোলার শিভালরাস প্রচেষ্টায়।
সকলে যে-যার সিটে গ্যাঁট হয়ে বসলাম। জ্যাক ও অ্যালাস্টার সকলকে গুডমর্নিং করল। জ্যাক এঞ্জিনের চাবি ঘোরাল, বাসের ব্লোয়ার খুলে দিল–এমন সময়ে অ্যালাস্টার বলল, জাস্ট আ সেকেণ্ড জ্যাক।
দুটি অস্ট্রেলিয়ান মেয়ে পাশাপাশি সিটে বসে অস্টেণ্ড থেকে ব্রাসেলস-এ এসেছিল, তাদের সিটটি শূন্য।
হইহই পড়ে গেল। কোথায় গেল সুন্দরী মেয়ে দুটি? কিডন্যাপড হয়ে হয়ে গেল না তো?
অ্যালাস্টার সকলকে জিজ্ঞেস করল, কেউ কি তোমরা দেখেছ তাদের?
সকলেই সমস্বরে বলল, না। কেউই দেখেনি। ওদের যে-তলায় ঘর ছিল সে-তলার অন্যান্যরা ওদের বাথরুমে দেখেনি।
তবে?
ইংরেজ লোকরা ঘন ঘন ঘড়ি দেখতে লাগল।
অ্যালাস্টার নিরুত্তাপে ক্যাজুয়ালি বলল, দে ম্যাস্ট বি অন দেয়ার ওয়ে।
দশ মিনিট কাটল। তবুও তাদের পথ ফুরোল না।
ট্যুরের প্রথম দিনের সকালে এমন বিপত্তিতে অ্যালাস্টার বেচারা ঘেমে নেয়ে উঠল। দেরি। হলে সমস্ত দিনের প্রোগ্রামেরই দেরি হয়ে যাবে।
এমন সময়ে জ্যাক বলল, একবার নেমে দেখে এসো তো অ্যালাস্টার ব্যাপারটা কী?
অ্যালাস্টার লক্ষ্মী ছেলের মতো নেমে গেল।
ইংরেজ প্যাসেঞ্জাররা ঘড়ি দেখে দেখে বাঁ-হাতের বগলে ব্যথা করে ফেলল, তবু অস্ট্রেলিয়ান মেয়ে দুটির পাত্তা নেই।
আমার বাঁ-পাশে একজন বুড়ো ইংরেজ-বুড়ো মানে বছর ষাটেক বয়স হবে কিন্তু দেখতে একেবারে জোয়ানের মতো। তাঁর পাশে তাঁর স্ত্রী। আমার ঠিক পেছনে তাঁর শালা ও শালা-বউ। আমার পাশের ভদ্রলোকের নাম জন ও তাঁর শালার নাম বব। শালা-ভগ্নীপতিতে গতকাল বেশ গল্প-গুজব করতে করতে এসেছেন। জনের মুখেই শুনেছি যে জন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ভারতবর্ষে ছিল।
জন এবার কাঁধ ফিরিয়ে ববকে বলল, আই নো দ্য অসীসহোয়েন আই ফট উইথ দেম সাইড বাই সাইড। বিলিভ মি–দিজ ফেলাস আর অ-ফুলি স্লো।
যে-সময়ে বেরুনোর কথা ছিল সে সময় থেকে পনেরো মিনিট পেরিয়ে গেল।
এমন সময়ে যাত্রাপার্টির ছোকরার মতো বাবরি চুল ঝাঁকিয়ে অ্যালাস্টার হোটেলের অফিস থেকে দৌড়ে বেরিয়ে এল।
এসে বাসে উঠল দরজা খুলে।
হোয়াটস-দ্য ম্যাটার?
সমস্বরে অনেকে শুধোল অ্যালাস্টারকে।
জন বলল, এনি নিউজ?
অ্যালাস্টার গোবেচারার মতো মাথা নাড়িয়ে জানাল, হ্যাঁ। তালাস মিলেছে।
কোথায়? সকলে প্রায় একই সঙ্গে বলে উঠল।
অ্যালাস্টার বলল, ওঁরা ঘুমিয়ে আছেন। হোটেলের মালকিন ওদের তুলতে গেলেন এইমাত্র।
আর যাবে কোথায়?
বলার সঙ্গে সঙ্গে বাসের মধ্যে প্যাণ্ডেমনিয়ম। সাত জাতের লোকে ভরতি বাস। তাদের বিভিন্ন নোট অফ এক্সক্লামাশানে বাস ভরে উঠল। মহিলারা সবচেয়ে ক্রুদ্ধ হলেন। আমার ভাবগতিক দেখে মনে হল মেয়ে দুটো যখন বাসে উঠবে তখন এঁরা হয়তো আস্ত চিবিয়ে খাবেন ওদের।
না–চিবিয়ে খাওয়া ক্যানিবালদের ধর্ম। একটা ভদ্রগোছে রফা হল। বব প্রস্তাব তুলল যে ওরা যখন বাসে উঠবে তখন সকলে হাততালি দিয়ে ওদের অপমান করবে। প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হল।
হঠাৎ দেখি আমার পিঠে কে টোকা মারছে।
তাকিয়ে দেখি, বব-ওর গোল্ড-ব্লক পাইপের তামাকের কৌটোটা খুলে ধরে আমাকে বলছে, হ্যাভ আ ফিল।
আমিও খুশি হয়ে ওই তামাকে পাইপটা ভালো করে ভরলাম।
এই ট্যুর নাম্বার টু-টোয়েন্টির প্রথম সংকটে আমরা ববকে দলের নেতা নির্বাচন করলাম। এর পরেও বহু সংকটে বব নেতাজনোচিত অনেকানেক কাজ করেছিল। নেতার মতো নেতা। ঠাণ্ডা মাথা, স্বার্থপরতা নেই, বিপদের মুখে সবচেয়ে আগে দৌড়ে যায়, সকলের চেয়ে বেশি কষ্ট করে। ববকে নেতা মানতে অন্তত আমার কোনো দ্বিধা ছিল না।
আমরা সকলেই আজ যে বাস ছাড়বে, সে আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলাম। আমার মনে পড়ছিল পালকের নরম বালিশ আর লেপটার কথা। আরও আধ ঘণ্টা জমিয়ে ঘুমনো যেত! এই অ্যালাস্টারটার যত পাকামি।
এমন সময়ে দেখা গেল তাঁরা আসছেন।
গতকাল থেকে এত জনের ভিড়ের মধ্যে ওরা কারো চোখে পড়েনি। আজ বাস-ভরতি লোক–ওদের দুজনকে শ্যোনদৃষ্টিতে দেখতে লাগল।
একজন বেশ লম্বা। দারুণ ফিগার। ভারি মিষ্টি দেখতে। অন্যজন অত লম্বা নয় কিন্তু দুষ্টু দুষ্টু নীল চোখ; একটু মোটার দিকে। দুজনেরই পরনে খাকি-রঙা কডুরয়ের ট্রাউজার ও ফুলহাতা সোয়েটার। লম্বাজনের সোয়েটারের রং হালকা খাকি, বেঁটেজনের গাঢ় খয়েরি।
ওরা বাসে উঠতেই একসঙ্গে সকলে হাততালি দিতে লাগলেন।
যে মেয়েটি লম্বা সে ভারি লজ্জা পেল। লজ্জানত মুখ নামিয়ে সে নিজের সিটে গিয়ে বসল –আই অ্যাম অ-ফুলি সরি বলতে বলতে। কিন্তু তার সঙ্গিনীর চোখে আগুন ছিল। ভাবটা, দেরি করেছি, আমাদের উঠিয়ে দেওয়া হয়নি কেন?
যাই-ই হোক, অবশেষ বাস ছেড়ে দিল। একটু পরই জঙ্গলে এসে পড়লাম। Soignes-এর জঙ্গল পেরিয়ে দেখতে দেখতে আমরা Overise হয়ে Wavre হয়ে Gembloux হয়ে নামুর-এ এসে পৌঁছোলাম।
নামুর-এ পোঁছে চা বা কফি খাওয়ার জন্যে দশ মিনিট বাস দাঁড়াল। সকলে নেমে চা বা কফি খেল।
নামুর থেকে রওয়ানা হয়ে Arlon-এ আসা গেল। তারপর বেলজিয়ামের সীমানা পেরিয়ে গ্র্যাণ্ড ডাচী অফ লাক্সেনবার্গ-এ এসে পৌঁছোলাম। গ্র্যাণ্ড ডাচীর রাজবাড়িটি পথের বাঁ-পাশে পড়ল। অ্যালাস্টার কমিউনিকেশন সিস্টেমে বলতে বলতে চলেছে–বাসও চলেছে পথের পর পথ–জেলার পর জেলা পেরিয়ে।
সেখানেই লাঞ্চ খাওয়া হল। এখানে এখনও ফিউডাল প্রথা চালু আছে। লাক্সেনবার্গের মতো ছিমছাম ছোটো একটা রাজ্যের রাজা হওয়া গেলে মন্দ হত না।
যেভাবে দেশের পর দেশ পার হয়ে আসছি যে, আমার মনে হল বর্ধমান থেকে বাঁকুড়া কি বহরমপুর থেকে সিউড়ি আসতে বুঝি কতই না দেশ পার হতে হত।
লাঞ্চ বলতে একটা স্যুপ, একটুকরো চশমা করে কাটা বিফস্টেক-রীতিমতো আণ্ডার ডান অর্থাৎ আধ-সেদ্ধ। সায়েবরা নাকি আণ্ডার-ডান বিফস্টেকই পছন্দ করে বেশি। হবে হয়তো। আমার তো মোটে ভালো লাগে না। তবে, পরে বুঝেছিলাম পেটে থাকে অনেকক্ষণ এবং খেলে শীতটাও বুঝি একটু কম-কম মনে হয়।
ওখান থেকে রওয়ানা হয়ে ফ্রান্সের লোরেন ও আলসাক ব্রডিন্স দিয়ে বাস চলতে লাগল।
অ্যালাস্টার বলল, বিকেলে আমরা স্ট্রসবার্গ হয়ে রাইন নদী পেরিয়ে জার্মানিতে ঢুকব। রাইন এখানে ফ্রান্স ও জার্মানির মধ্যে দিয়ে বয়ে গেছে।
কখন রাইন নদী দেখব, কখন দেখব করে হা-পিত্যেশ করে বসেছিলাম। কিন্তু যখন অ্যালাস্টার বলল, ওই যে দেখা যায় তখন আমার বরিশালের মাধবপাশা গ্রামের দীঘির পারে শোনা এক কীর্তনীয়ার কীর্তনের কথা মনে পড়ল।
রাইনের সাঁকোর ওপর যখন বাসটা এল তখন অ্যান্টি-ক্লাইম্যাকসের চূড়ান্ত এই যে দেখি। আমাদের কালীঘাটের গঙ্গার চেয়ে একটু বড়ো এক ঘোলাজলের নদী।
হঠাৎই সেই মুহূর্তে আমার বড়ো গর্ব হল আমার সুন্দর দেশটার জন্যে। কী সুন্দর আমাদের দেশটা–কত ভালো আমাদের দেশের সাধারণ লোকেরা–শুধু আমরা যদি, আমরা যদি, এদের মতো দেশকে ভালোবাসতাম, দেশের ভালোকে ভালোবাসতাম, যদি শুধু ভঙ্গি দিয়ে চোখ না ভোলাবার চেষ্টা করতাম! কী না করতে পারি আমরা এখনও আমাদের দেশটাকে নিয়ে। যদি সময় থাকতে বুঝতে পারতাম যে দেশটা সকলের প্রত্যেকের দেশটা কোনো গোষ্ঠী বা পরিবারের বা একাধিক রাজনৈতিক দলের নয়–তাহলে কী ভালোই না হত।
রাজা লিওপোল্ড-এর রাজত্ব ছেড়ে আসার পর চা খাওয়ার জন্যে যে প্রকান্ড অথচ জনবিরল একতলা রেস্তোরাঁতে আমাদের বাস পনেরো মিনিটের জন্যে থামানো হয়েছিল, তার বিরাটত্ব রীতিমতো চমৎকৃত করেছিল।
রেস্তোরাঁ না হয়ে খুব সহজেই জায়গাটা পাবলিক হল হতে পারত। ডায়াসের ওপর একটা অটোমেটিক বিদ্যুৎ চালিত অর্কেস্ট্রা বাজছে। ডায়াস ও বসার বন্দোবস্ত দেখে মনে হল এখানে নিশ্চয়ই গান বাজনা ইত্যাদি হয়ে থাকে।
সকালে অস্ট্রেলিয়ান মেয়ে দুটি আমাদের দেরি করিয়ে দেওয়া ছাড়াও সে-সকালেই আরও একটা কান্ড ঘটেছিল।
পরশু রাতে ব্রাসলস শহরে ঘুরে বেড়াবার সময় আমাদের একটা লেসের দোকানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সুন্দর সব লেসের কারুকাজ। টেবল ক্লথ, পর্দা, টেবল ম্যাটস আরও কত কী। কিন্তু আমাদের দলের একজন আমেরিকান মহিলা–মিস ফাস্ট তাঁর পাসপোর্ট হারিয়ে ফেলেছিলেন। লেস কেনার জন্যে টাকা বের করার সময়ে বোধহয় পাসপোর্ট পার্স থেকে দোকানেই পড়ে গেছিল। তাই সকালে রওয়ানা হয়েই প্রথমে আমরা সেই দোকানের সামনে এলাম সবচেয়ে আগে। কিন্তু শোনা গেল যে দোকান খুলবে সাড়ে আটটায়। জ্যাক আর অ্যালাস্টার বিনা বাক্যব্যয়ে সেই মহিলাকে মালপত্র সমেত ওই দোকানের সামনে নামিয়ে দিল। বলে গেল যে, যদি পাসপোর্ট পাওয়া যায় তাহলে নিজ-খরচায় ট্রেনে করে যেন Denzlingen-এ চলে আসেন, সেখানে আমরা রাতে থাকব। Denzlingen জার্মানিতে বেলজিয়ামের রাজধানী ব্ৰাসলস থেকে ওই জায়গায় পৌঁছোতে হলে বেলজিয়াম ছেড়ে ফ্রান্স হয়ে তারপর জার্মানিতে ঢুকতে হবে।
ভদ্রমহিলার বয়েস পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন হবে কিন্তু চেহারা ও সাজগোজের ঘটায় বয়েসটাকে রং চাপা দিয়ে রাখা হয়েছে। আমেরিকান ওয়েস্টার্ন ছবিতে ব্যাং ব্যাং করে দু-হাতে পিস্তল ছুঁড়তে ছুঁড়তে ঘোড়ায়-চড়ে আসা, সেলুনে ঠ্যাং ছড়িয়ে চুল কাটতে কাটতে বিয়ার খাওয়া নায়কদের সঙ্গে যে চেহারা ও সাজপোশাকের নায়িকাদের লটর-পটর করতে দেখা যায় এই ভদ্রমহিলার হাবভাব, সাজগোজ, চেহারা-ছবি হুবহু সেইরকম।
বাসটা যখন সেই দোকানের সামনে থেকে চলে এল, বাসের বেশির ভাগ প্যাসেঞ্জারই তাঁর দিকে ফিরেও তাকাল না। ইতিমধ্যেই লক্ষ করেছিলাম যে, বয়স্ক ও রক্ষণশীল ইংরেজ প্যাসেঞ্জাররা তাঁদের স্ত্রীদের সঙ্গে ওঁকে নিয়ে প্রথমদিন থেকেই গুজগুজ ফুসফুস করতে আরম্ভ করেছিলেন। ইংরেজরা, বোধহয় একমাত্র ইংরেজরাই, এত আস্তে ফিসফিস করে কথা বলতে পারে যে, পাশের লোকও সেকথা শুনতে পায় না। এদের দেশের ফুলশয্যা ব্যাপারটা যদি থাকতও তবে মহিলাদের এ বাসর জাগার তাবৎ উৎসাহই মাঠে মারা যেত।
আমার মনে হল ভদ্রমহিলার সঙ্গে আমাদের সকলেরই চিরতরে বিচ্ছেদ ঘটল, তাই স্বাভাবিক দয়া ও ভদ্রতার খাতিরে কাঁচের মধ্যে দিয়ে হাত তুললাম।
কিছু কিছু সহযাত্রীও হাত তুলে বাই-বাই করল।
মেজোল পেরিয়ে এসে বিকেলে চা খেতে দাঁড়িয়েছিলাম ফ্রান্সের Alsop জেলার ছোটো শহর Metz-এ। ওয়েট্রেস ট্রে হাতে করে পড়ি-কি-মরি করে দৌড়াতে দৌড়োতে পাঁদো পাঁর্দো আওয়াজ করছে মুখে। জঙ্গলে হাঁকোয়াওয়ালার তাড়া খেয়ে পালানোর সময়ে অনেক সময়ে শজারু ওইরকম অদ্ভুত আওয়াজ করে।
অনুসন্ধান করে জানা গেল যে, ইংরিজি বেগ ইওর পাৰ্ডন-এর ফরাসি প্রতিশব্দ পাঁদো মঁসিয়ে। তাড়াতাড়িতে আর মঁসিয়ে মাদাম, মাদমোয়াজেল, কিছুই বলার সময় না পেয়ে গাঁক গাঁক করে পাঁর্দো পাঁদো, বলতে বলতে বেচারারা দৌড়াদৌড়ি করছে।
কী ইংল্যাণ্ডে, কী পৃথিবীর পশ্চিম-দেশীয় অন্যান্য যে-কোনো প্রান্তে, যা সবচেয়ে আগে চোখে পড়ে তা ওদের কর্মব্যস্ততা। সব কাজই কত তাড়াতাড়ি করে ওরা। দৌড়াদৌড়ি করে মাত্র দুজন ওয়েট্রেস পঞ্চাশজন লোককে দেখাশুনো করে চা-পেস্ট্রি খাইয়ে দেবে পনেরো মিনিটে। চেঁচামেচি নেই, হই-হল্লা নেই, খরিদ্দারদের মধ্যেও কারোই এমন মনোভাব নেই যে, দোকানে চা খাচ্ছি তো মাথা কিনে নিয়েছি মালিক ও ওয়েটার-ওয়েট্রেসদের। একমিনিট সময়ও যে নষ্ট করার নয়-কাজের সময় কাজ তাড়াতাড়ি না শেষ করলে যে খেলার সময় পাওয়া যায় না, তা ওরা বড়ো ভালো করে বুঝেছে। ওরা সময়ের আগে আগে দৌড়োতে চায় যেন। তাই-ই ওরা এত কাজও করে এত মজাও করে।
স্ট্রসবার্গ বেশ বড়ো শহর। রাইনের ওপরেই বড়ো বন্দর। বছরে দশ মিলিয়ন টন কার্গো ওঠা-নামা করে এ বন্দরে। অসবর্ন ছাড়িয়ে এসে আমরা জার্মানিতে যখন পড়লাম ততক্ষণে সন্ধে হয়ে এসেছে। অটো-বান ধরে মাইল পঁয়তাল্লিশ এসে আমরা Denzlingen-এ পৌঁছোলাম। এটা ছোটো একটি গ্রাম। ছোটো গ্রাম হলে কী হয় এমন গ্রামেও এমন সব হোটেল আছে যে, পঞ্চাশজন লোকের থাকা-খাওয়ার বন্দোবস্ত অচিরে করে ফেলে এরা।
স্যুটকেস নামিয়ে নিয়ে ঘরে গেলাম হাত-মুখ ধুয়ে একটু পা ছড়িয়ে নিতে। অ্যালাস্টারের হুকুম হল পনেরো মিনিট পর সকলকে ডাইনিং রুমে নেমে আসতে হবে একতলায় ডিনার খেতে।
রোজ সাতটায় ডিনার খেয়ে রীতিমতো সাহেব হয়ে উঠছি দেখলাম। কিন্তু সাহেবেরা শেষরাতে যখন পেট চু চু করে তখন কী খায় তা জানতে ইচ্ছে করে। আমাদের দেশের মতো, চিড়ে আর পাটালি গুড় পাওয়া যায় না ওদের দেশে।
কিছুক্ষণ পর ডাইনিং রুমে নেমে আসতেই দেখি ঘর আলো করে মিস ফাস্ট বসে আছেন; মুখের মেক-আপ একটুও ওঠেনি–হালকা সবুজ গোড়ালি পর্যন্ত পোশাক, গাঢ় সবুজ আই-ল্যাশ, বাঁ গালের কৃত্রিম বিউটি স্পটসমতে ডান পায়ের ওপর বাঁ-পা তুলে তিনি দিব্যি খোশমেজাজে বসে আছেন।
পাসপোর্ট হারিয়ে যাওয়ায় চেয়ে বড়ো দুর্ঘটনা বিদেশে ভাবা যায় না। তাই এই পঞ্চাশোর্ধ্ব তরুণী মহিলার সম্পূর্ণ অবিচলিত ও উত্তেজনাহীন মনোভাব সকালে আমাকে চমৎকৃত করেছিল। আমার নিজের পাসপোর্ট ট্যুর-এর মধ্যে হারিয়ে ফেললে কী করতাম ভাবতেও আতঙ্কিত হচ্ছিলাম। সে কারণে, অবাকই হলাম যে, পাসপোর্ট শুধু উদ্ধার করেছেন তাই-ই নয়; আমরা বাসে এসে পৌঁছোনোর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বেলজিয়াম থেকে ফ্রান্স, সেখান থেকে জার্মানির এই গ্রামে দিব্যি পৌঁছিয়ে গিয়ে হাসি হাসি মুখে দেদীপ্যমান রয়েছেন।
ক্যারল ও জেনি, সেই অস্ট্রেলিয়ান মেয়ে দুটি সকালের লজ্জা বেমালুম ভুলে গিয়ে দুটি সুদর্শন, লম্বা জার্মান ছেলের সঙ্গে একটেবিলে বসে দিব্যি হাসিমুখে গল্প করছে। ওদের দুজনকেই খুব উচ্ছল দেখলাম। কারণটা পরে জানলাম। ওরা আজ ডিনার খেয়ে নিয়ে হোটেলের ঘরে থাকবে না। ছেলে দুটি একটি ভোকসওয়াগেন ট্যুরার গাড়ি নিয়ে এসেছে সেই গাড়িতেই ওদের সঙ্গে ওরা রাত কাটিয়ে ভোরে চলে যাবে ওদের সঙ্গে মুনিকে। সেখানে বিশ্ববিখ্যাত বিয়ার ফেস্টিভ্যাল হচ্ছে এখন। বিয়ারের প্রস্রবণ ওঠে সেখানে। Steifel-এ করে ওরা সেই প্রস্রবণ থেকে সারারাত বিয়ার খাবে–হইহই করবে, মেলা দেখবে। তিনদিন তিনরাত হই-হুঁজ্জোত করে আবার আমাদের সঙ্গে মিলবে এসে সুইটজারল্যাণ্ডে। Steifel গামবুটের মতো দেখতে কাঁচের বুট–তাতে করে জার্মানরা বিয়ার খায়। একবুট বিয়ার দু-হাতে ধরে তুলে চোঁ-চোঁ করে গিলে ফেলে।
ধন্যি রাজার ধন্যি দেশ!
ডিনার সার্ভ করতে লাগল দুটি জার্মান মেয়ে। সুপ প্রথমে। তারপর মাছভাজা সঙ্গে স্যালাড ও টার্টার সস। তার সঙ্গে টক বাঁধাকপি, গাজর শসা ও বিট দিয়ে তৈরি স্যালাড। পরিশেষে আনারসের পাই। খাওয়ার আগে Denzlingen-এর স্থানীয় বরুয়ারীর লাগার বিয়ার ও ওয়াইন পান করা গেল কিঞ্চিৎ।
খাওয়া শেষ হতে না হতেই ম্যানেজার এসে বলল, তোমার টেলিফোন এসেছে লানডান থেকে। ফোন ধরতেই দেখি টবী।
ওপাশ থেকে বলল, খী খারবার–আমাদের ভুলে গেলে দেখছি। আছ কেমন? কী খেলে? কোনো অসুবিধা হচ্ছে না তো?
একসঙ্গে এত প্রশ্নের জবাব দেওয়া যায় না বলে উত্তরগুলো খিচুড়ি পাকিয়ে এককথায় বললাম, খাসা আছি।
ও বলল, ক্লান্ত লাগছে?
না তো! অবাক হয়ে বললাম।
ও বলল, লাগবে।
তারপর বলল, ভয় নেই। তোমার জন্যে বিছানা রেডি করে রাখব। ভিক্টোরিয়া স্টেশানে তোমাকে নিয়ে যাব আমরা। এখানে দু-দিন রেস্ট করে ঘুমিয়ে তারপর টরোন্টো যেয়ো। এই ট্রগুলোরীতিমতো টায়ারিং।
এখনও বুঝতে পারছি না। আমি বললাম।
টবী কসমস-এর লানডান অফিসে ফোন করে ইটিনিরারী জেনে নিয়েছিল। আমরা কবে কখন কোন হোটেলে পৌঁছোব, রাত কাটাব সব ও জানে। আর পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ফোন করা তো কোনো ব্যাপারই নয়। সমস্ত জায়গার একটা করে এরিয়া-কোড আছে। সমস্ত জায়গা থেকে সমস্ত জায়গাতেই প্রায় ডাইরেক্ট ডায়ালিং-এর প্রথা আছে। শুধু এরিয়া কোড ঘুরিয়ে নাম্বার ডায়াল করলেই মুহূর্তের মধ্যে অন্য প্রান্তে কথা বলা যায়। ট্রাঙ্ক অপারেটরের মুখঝামটা নেই। টিকিট নম্বর মুখস্ত করে রাখার ঝামেলা নেই। কলকাতা থেকে আশি মাইল দূরে ট্রাঙ্কল করতে গিয়ে কল বুক করে বসে থেকে ভগবান ও অপারটেরদের কাছে করজোড়ে ভিক্ষা চাওয়া নেই।
আমাদের দেশের, বিশেষ করে কলকাতার টেলিফোন বিভাগের লজ্জাকর অপদার্থতা মনে পড়ছিল। আমাদের সবই সহ্য হয়, বাঙালিদের মতো সহ্যশক্তি ক্রীতদাসদেরও ছিল না বোধহয়। আমাদের দেশের সরকার ভগবান. সব সমালোচনার ঊর্ধ্বে তাঁরা। সরকারের কানে তুলো, পিঠে কুলো। লাজলজ্জা সব কিছুই ধুয়ে মুছে তারপই রাজনীতি করেন আমাদের সরকার পক্ষের এবং সরকার বিরোধী রাজনীতিকরা। যাঁরা বলেন আমাদের দেশের সবই খারাপ, আমি তাঁদের দলে ছিলাম না। আবার যাঁরা বলেন যে, আমাদের দেশের সবই ভালো, আমাদের সব কিছুই সমালোচনার উর্ধ্বে–আমাদের গণতন্ত্র ও নেতারা সবই দেবদুর্লভ ও দেবসুলভ, আমি তাদেরও দলে নেই। ভালোটা ভালোই, খারাপটাও খারাপ। আমি আমার দেশকে ভালোবাসি তাই দেশের ভালোত্বে যেমন গর্বিত হই খারাপত্বে তেমনই দুঃখিত হই। দেশটা আমার যতখানি, নেতাদের বা কোনো রাজনৈতিক দলেরও ততখানিই। একথা বলতে যদি কেনো বিশেষ স্বাধীনতার দরকার হয় তবে বাঁচা-মরায় তফাত দেখি না কোনো। যে স্বাধীনতা নিয়ে আমি জন্মেছি বলে আমি বিশ্বাস করি–সেই স্বাধীনতা কারও কৃপণ ও ভন্ড হাতের দয়ার দান হিসেবে আমি গ্রহণ করতে রাজি নই।
যেসব দেশ উন্নত হয়েছে তাদের দেশের সাধারণ মানুষদের জন্যেই উন্নত হয়েছে। সাধারণ মানুষেরা আত্মসচেতন, কর্মঠ, আত্মসম্মানজ্ঞানী না হলে, নিজের নিজের স্বাধীনতায় বিশ্বাস না করলে, নিজের নিজের স্বাধীনতার ন্যায্য মূল্য দিতে প্রস্তুত না থাকলে তারা এত উন্নত হত না। তাদের অগ্রগতি–এত ঝড়-ঝাঁপটা যুদ্ধ-বিগ্রহর পরও তাদের মাথা তুলে দাঁড়ানোর কারণ তারা নিজেরাই। কোনো দল বা নেতা তাদের কোলে করে বিশল্যকরণী গিলিয়ে দেয়নি। তেমন নেতাগিরিতে তারা বিশ্বাসও করেনি কখনো।
ফোন ছেড়ে দিয়ে বাইরের নির্জন পথে, ওভারকোটের কলার তুলে দিয়ে পকেটের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমার হঠাৎই বহুদিন আগে পড়া, ওয়াল্ট হুইটম্যানের লিভস
অফ গ্রাস-এর ক-টি লাইন মনে পড়ে গেল :
All doctrines, all politics and civilization exurge from you. All sculpture and monuments and anything inscribed anywhere are tallied in you.
The gist of historics and statistics as far back as the records reach is in you this hour-and myths and tales the same.
If you were not breathing and walking here where would they all be?
আমি, তুমি, আপনি, আমরা প্রত্যেকে প্রচন্ডভাবে বেঁচে আছি, বেঁচে থাকা উচিত। আমাদের নিজেদের প্রত্যেকের নিজের জন্যে; আমাদের গর্বিত, দুঃখিত, অপমানিত বোধ করা উচিত। আমরা, এই খন্ড খন্ড আমরাই একটা পুরো দেশকে বড় করতে পারি, জাগিয়ে তুলতে পারি–সত্যিকারের গর্বিত বোধ করতে পারি নিজেদের উদ্দেশ্যের সততা ও আন্তরিকতার জন্যে এবং আমরাই নিজেদের মিথ্যা দম্ভ, উদ্দেশ্যসাধনের ভন্ড ও মিথ্যা ও পন্ডিতমন্য প্রচেষ্টার গ্লানিতে নিজেদের থুথুতে নিজেদের সিক্ত করতে পারি। আমারটা আমার ভাবার, আমারই করার। আমার একার। তোমারটাও তাই। আপনারটাও।
হঠাৎ, হঠাই, বহুদিন পর আরও ক-টি লাইন মনে পড়ে গেল, এই একলা রাতে, শীতার্ত কিন্তু স্বাধীন, উন্নত ও গর্বিত এক দেশের মাটিতে হাঁটতে হাঁটতে। মনে হল, লাইনগুলো হঠাৎ যেন আমাকে বিদ্ধ করল।
Long enough have you dreamed contemptible dreams.
Now I wash the gum from your eyes.
You must habit yourself to the dazzle of the light and of every moment of your life.
Long have you timidly worded, holding a plank by the shore.
Now I will you to be a bold swimmer.
To jump off in the midst the sea, and rise again and nod to me and shout, and laughly dash with you hair.
ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠেই প্রাতরাশ সেরে নিয়ে যখন বাসে উঠলাম তখন আকাশে মেঘের ঘনঘটা। দেখতে দেখতে আমরা জার্মানির বিখ্যাত Black forest এলাকায় চলে এলাম। এই জঙ্গল নিয়ে শুধু এদেরই কেন পুরো ইয়োরোপের খুব গর্ব। হায়! ওরা আমাদের দেশের জঙ্গল দেখেনি। দেখেনি ডুয়ার্সের জঙ্গল, দেখেনি উড়িষ্যার মহানদীর অববাহিকার জঙ্গল–ওরা কি বুঝবে জঙ্গল কাকে বলে? সেটা কোনো কথা নয়, আসলে যেটা জানতে ভালো লাগে যে ওরা জঙ্গল খুব ভালোবাসে। যান্ত্রিক সভ্যতার শেষধাপে এসে মঙ্গলগ্রহে মাটি খোঁড়াখুঁড়ি করতে করতেই দিনের পর দিন ওদের মনে এই ধারণাই বদ্ধমূল হচ্ছে যে, প্রকৃতিই শেষ অবলম্বন। যতই সে উন্নত, সভ্য, শিক্ষিত বোধ করুক না কেন তাকে শেষে প্রকৃতির কাছে ভালো লাগার জন্যে, ভালোবাসার জন্যে ফিরে আসতেই হবে।
ব্ল্যাক ফরেস্ট ফার-এর জঙ্গল। গাছগুলোর গায়ে শ্যাওলা জমে আছে। কিছু কিছু অর্কিড। ঘন সবুজ রং বলে গাছগুলোকে কালো মনে হয়–তাই এই নাম। ব্ল্যাক ফরেস্টের মাঝামাঝি এসে বৃষ্টি নামল। ওদের দেশের বৃষ্টির সঙ্গে আমাদের বর্ষার কোনো তুলনা চলে না। বৃষ্টিও যেন বড়ো বেশি নিয়মানুবর্তী–আমাদের বর্ষার মেজাজ ওদের দেশের বর্ষার নেই। রবীন্দ্রনাথ ওদেশে জন্মালে আমরা এত বিভিন্ন গান পেতাম না, আমাদের শাস্ত্রীয় সংগীতে এত বর্ষার রাগ-রাগিণী বর্ষাবরণের আনন্দে অধীর হয়ে জন্মাত না।
জঙ্গলের মধ্যে মধ্যে ছবির মতো সব গ্রাম।
এই ছবি-ছবি ব্যাপারটাও আমার মোটে পছন্দ নয়। আমার গরিব দেশের গ্রাম অগোছালো এলমেলো। অনেক কষ্ট সেখানে, কিন্তু গোরুর গায়ের গন্ধ, জাবনার গন্ধ, ব্যাঙের ডাক, বাঁশবনে জোনাকি জ্বলা, মেঠো পথ, হলুদ-বসন্ত পাখির উড়ে যাওয়া ওদের নেই। ওরা সুখ খুঁজতে গিয়ে সুখকে একেবারে মাটি করে বসে আছে। সুখ কাকে বলে ভুলে গেছে ওরা আরামের কবরে।
অ্যালাস্টার একটা গ্রাম দেখিয়ে বলল–দেখুন এই গ্রাম থেকে ড্যানিউব নদী বেরিয়েছে।
নর্দমার মতো ড্যানিউব দেখলাম। ব্লু-ড্যানিউব বলে এক বিখ্যাত রেকর্ড শুনেছি। বহুবার সেই রেকর্ড শুনতে শুনতে চোখের সামনে যে নদীর ছবি ফুটে উঠেছে বার বার কল্পনায়, তার সঙ্গে এ নদীর চেহারা একেবারেই মেলে না। আমাদের দেশের হোগলা-বাদার পাশে পাশে এমন নর্দমা আকছার দেখতে পাওয়া যায়। নদীমাতৃক দেশের লোককে ইয়োরোপের নদীগুলো বড়ো হতাশ করে।
দূর থেকে লেক কনস্ট্যান্স দেখা যাচ্ছিল। এই হ্রদের একপাশে জার্মানি অন্যদিকে অস্ট্রিয়া আর সুইটজারল্যাণ্ড। লেক কনস্ট্যান্টলি রাস্তার ডানদিকে থাকল। লেকের ওপারে সুইটজারল্যাণ্ডের পাহাড়গুলো-আল্পস-এর রেঞ্জ দেখা যাচ্ছিল। লেকের পাশে পাশে কত যে ছবির মতো গ্রাম, হোটেল, কফি-হাউস তার লেখাজোখা নেই। জার্মানি ও অস্ট্রিয়ার মতো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দেশ বোধহয় ইয়োরোপেও নেই।
লেক কনস্ট্যান্স বাঁ-দিকে রেখে আমরা জার্মানির বর্ডার পার হয়ে অস্ট্রিয়াতে এসে পড়লাম। তারপর Brener Pass (৭০০০ ফিট উঁচু)-এর দিকে এগোতে লাগলাম। ব্রেনার পাস পেরিয়ে ইটালিতে ঢুকব বলে।
ইতিমধ্যে ইজরায়েলের উনিশ বছরের মেয়ে সারার সঙ্গে আমার বেশ বন্ধুত্ব হয়েছে। নীল চোখ–যেন কত কী স্বপ্ন, প্রত্যাশা, প্রতিজ্ঞা সব লেখা রয়েছে চোখের তারায়। কথা কম বলে, কিন্তু যখন বলে তখন ভারি বুদ্ধিমতী ও রসিকা। এ ক-দিন আমার সঙ্গে কথা হয়নি একটাও। গায়ের রং বাদামি দেখে দুশমন গেরিলা-টেরিলা ভেবে থাকবে হয়তো। কিন্তু গত রাতে খাওয়ার টেবিলে ওর সঙ্গে আলাপ হয়েছে ভালো করে। রাজনৈতিক কারণে দেশে দেশে অনেক বিভেদ ও মনোমালিন্য হতে পারে, হয়; কিন্তু কোনো দেশের ব্যক্তির সঙ্গে অন্য ব্যক্তির মানুষ হিসেবে খোলাখুলি মেলামেশায় কোনো বৈরিতা বা আড়ষ্টতা হওয়া বা থাকা উচিত বলে আমার মনে হয় না। আমরা সকলেই তো একই মানবজাতির অংশ। যে হারে গ্রহ-গ্রহান্তরে পৃথিবীর মানুষ নাক গলাতে শুরু করেছে এইচ. জি. ওয়েলস-এর দূরদৃষ্টি সম্পন্ন লেখা ওয়ার অফ দি ওয়ার্ল্ডস সত্যি হয়ে উঠতে পারে যে-কোনো দিন। মঙ্গলগ্রহের সঙ্গে পৃথিবীর যুদ্ধ বাধলে রাশিয়া-আমেরিকা ও আরব ইজরায়েল পাশাপাশি লড়াই করে কি করে না দেখা যাবে। মাঝে মাঝে মনে হয় এমন একটা গ্রহে গ্রহে যুদ্ধ তাড়াতাড়ি লেগে যাওয়া দরকার অন্তত মনোমালিন্য ভুলে গিয়ে–তাতে এই পৃথিবীর সাদা কালো-হলদে-বাদামি মানুষগুলোনিশ্চয়ই আরও কাছাকাছি ঘেঁষাঘেঁষি আসবে একে অন্যর তারা বুঝবে যে আমরা সকলেই মানুষ-এর চেয়ে বড়ো বা এ ছাড়া অন্য পরিচয় আমাদের কিছুই নেই।
হঠাৎ কাঁধে টোকা পড়ল। আমাদের সর্বসম্মতিক্রমে এবং বিনা ভোটে নির্বাচিত ইংরেজ টেকো-লিডার কাঁধ ট্যাপ করছেন।
ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাতেই বললেন–হাউ বাউট আ ফিল?
আমি হাত বাড়িয়ে ওঁর গোল্ড-ব্লক ট্যোবাকোর টিনাটা নিলম। পাইপ ভরব বলে। আমাদের নেতার চেয়ে নেতার স্ত্রী আমার বেশি ভক্ত হয়ে উঠেছিল। আগেই বলেছি, নেতা আমাদের পেশায় ছুতোর। আমি গবির লোক, গরিব দেশের লোক, তাই টবী-ভাইয়ের দাক্ষিণ্যে যে ট্যুরে ইয়োরোপ দেখতে এসেছি সেটা সবচেয়ে গরিবদের ট্যুর। আমার বাসের কমরেডরা ছুতোর কামার বাস-ড্রাইভার গরিব ট্যুরিস্ট ছাত্র-ছাত্রী ইত্যাদি।
এই টেকো সাহেব তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে জীবনের পঞ্চান্ন বছর কঠোর পরিশ্রম করে তবে এতদিনে ইংল্যাণ্ড থেকে কন্টিনেন্টে আসার মতো পাথেয় জোগাড় করতে পেরেছেন। সব দেশেই গরিব বড়োলোক আছে। ব্যাপারটা আপেক্ষিক। কিন্তু ওদের দেশের যা অর্থনৈতিক মান তাতে যে দম্পতি পঞ্চান্ন বছরের আগে ইংল্যান্ড থেকে কন্টিনেন্টে আসার মতো পাথেয় জোগাড় করে উঠতে না পারেন তাঁদের অবস্থা ভালো নয়ই বলতে হবে। সে কারণেই এতদিনে আসতে পেরে ওঁদের আনন্দের আর অন্ত নেই। নিজের মেহনতের পয়সায় এসেছেন, কালোবাজারি বা ফাটকাবাজারি রোজগারের পয়সা নয়–এটাই বা কি কম আনন্দের?
মেমসাহেব প্রায়ই গুনগুনিয়ে গান গাইতেন। গলাটা ভারি মিষ্টি। এমন এমন সব হিট গান, বেশির ভাগই ফিল্মের গান যে ছোটোবেলায় আমরাও এদেশে তার কিছু কিছু গান শুনেছি।
আমি একবার মুখ ঘুরিয়ে ওঁকে বলেছিলাম–প্লিজ আস্তে গেয়ে আমাকে কষ্ট দেবেন না–একটু জোরে গান–এত ভালো গলা আপনার লুকিয়ে রাখার জন্যে নয়।
পরক্ষণেই দেখলাম মেমসাহেব গান থামিয়ে ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে পাউডারের কৌটো বের করে গালে লাগাচ্ছেন।
এতদিনে ইংরিজি প্রবচনের মানে বুঝলাম–To powder ones nose.
দেশ বা জাত নির্বিশেষে মহিলারা চিরদিন এ বাবদে মহিলাই থাকেন। কমপ্লিমেন্ট পেলে খুশি হন। যেসব পুরুষ জানেন ঠিক কী করে কমপ্লিমেন্ট দিতে হয় তাঁরা চিরদিনই সব বয়েসি সব-দেশি মহিলার কাছে সমান প্রিয়।
আমি কিন্তু জানি না। জানলে খুশি হতাম।
কী করে যে সময় উড়ে যায় বগারির ঝাঁকের মতো তার হিসেব রাখা দায়। লাঞ্চের জন্যে বাস থামল। মাঝে, পথে কফি-ব্রেকও হয়েছিল। জায়গাটার নাম মনে নেই। Dornbin নামের একটা ছোটো গ্রামের একটা ছোটো রেস্তোরাঁতে লাঞ্চ খাওয়া হল। চমৎকার চিকেনের স্যুপ, বিফ-স্টেক। শেষকালে পাইন-অ্যাপল পাই। সঙ্গে একটু করে জার্মান schnapps- সেই যে schnapps-এর কথা লিখেছিলাম আগে–টবীর সঙ্গে Tyroler Hut-এ সেই খেয়েছিলাম। লানডানের বেজওয়াটার স্ট্রিটে!
এই Dornbin-এর হোটেলে যে ছিপছিপে মেয়েটি আমাদের খাওয়া-দাওয়ার দেখাশোনা করছিল সে ভারি সুন্দরী। অস্ট্রিয়ান গাউন পরেছিল একটি। দেখতে অনেকটা–ম্যাকসির মতো–বুকের কাছে লেস বসানো, লাল-কালো কাজের। আমাদের বাসের ড্রাইভার জ্যাক তার সঙ্গে খুব ইয়ার্কি করছিল।
অ্যালাস্টার লাজুক শিক্ষিত ছেলে। মিষ্টভাষী। ও-ও গল্প করছিল মেয়েটির সঙ্গে। জানলাম, এই মেয়েটি এক সময়ে এই কসমস ট্যুরের অ্যালাস্টারের মতোই গাইডের কাজ করত। ট্যুর নিয়ে কয়েকবার এই হোটেলে এসেছিল। তখনই এই হোটেলের ইয়াং ও হ্যাণ্ডসাম অস্ট্রিয়ান মালিকের সঙ্গে আলাপ হয়। তারপর তাকে বিয়ে করে কসমস কোম্পানির আমাদের মতো সৌন্দর্যরসিক অনেক যাত্রীর সর্বনাশ করে অস্ট্রিয়ার এই সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশে থেকে যায়। ঘন নীল চোখ, ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি ও ব্যারনের রক্তসম্পন্ন তার স্বামীকে দেখে খুব হিংসা হচ্ছিল। এরকম স্ত্রী পাওয়া অনেক পুণ্য-কর্মের ফল। শুধু চেহারাই নয়, তার কথাবার্তা হাঁটাচলা সব মিলিয়ে তাকে তার সেই লাল-কালো গাউনে যেন একটি প্রজাপতি বলে মনে হচ্ছিল।
জ্যাক আমাদের দেখিয়ে দেখিয়ে ওর গালে একটা চুমু খেল জোর করে ধরে। মেয়েটি ঘুরে দাঁড়িয়েই জ্যাকের পিঠে দুম দুম করে কিল বসিয়ে দিল হাসতে হাসতে, গালাগালি করতে করতে।
ওদের দেশে কোনো মেয়েকে চুমু খেলেই সঙ্গে সঙ্গে তার সতীত্ব নষ্ট হয়ে যায় না এবং চুমু খেলেই ভালোবাসাও হয়ে যায় না।
এ ক-দিন চোখ কান খুলে দেখে-শুনে যা মনে হচ্ছে তাতে এই ধারণাই জন্মাচ্ছে যে, অদূর ভবিষ্যতে হয়তো ওদের দেশের চেয়ে আমাদের দেশেই বিবাহবিচ্ছেদ বেশি হবে। ওরা শরীরটাকে কখনো মনের চেয়ে বড়ো করে দেখে না। শরীর যাকে তাকে I Thank you বলার মতো ইচ্ছে করলেই দেওয়া যেতে পারে; দেয়ও ওরা। কিন্তু শরীরের মোহ কাটিয়ে উঠে যখন ওরা কাউকে ভালোবাসে তখন মন, রুচি, ব্যক্তিগত আরও অনেক ব্যাপারে অনেকখানি নিশ্চিন্ত হয়েই বিয়ে করে। আমরা যেহেতু এ ব্যাপারে একটা প্রচন্ডরকম ট্রানজিটরি সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি–এই ভাঙচুর আমাদের মেনে না-নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। তা ছাড়া আমাদের দেশের মেয়েদের সদ্যপ্রাপ্ত আর্থিক স্বাধীনতা এ ব্যাপারে খুব নগণ্য অংশ নেবে না বলেই মনে হয়। আমাদের ওখানেও স্ত্রী-পুরুষের মেলামেশা আরও অনেক সহজ হয়ে গেলে আমরাও To put the cart before the horse-এর মতো ভুল বোধহয় করব না। সেদিন ভালোবাসা বলতে ভালোবাসাকেই বোঝাব, মোহ নয়, কাম নয়; রোমান্টিক কল্পনামাত্র নয়–তার চেয়েও হয়তো গভীরতর এবং স্থায়ী কিছু।
লাঞ্চ সেরে বেরোতেই এক অবাক কান্ড দেখলাম।
দুপুর থেকেই বৃষ্টি হচ্ছিল
Brener pass-এর দিকে যতই এগোতে লাগলাম ততই দূরের পাহাড়চুড়োগুলোতে বরফ দেখা যেতে লাগল। এই সময় লক্ষ করলাম যে রাস্তায় কম করে দেড়শো-দুশো গাড়ি, মার্সিডিজ-বেঞ্জ, ভলভো, সিত্রয়, ওপেল, ফোর্ড; নানারকম ভোকসওয়াগেন, রোভার, রোলস-রয়েজ বনেটের ওপর একটা করে ফুলের তোড়া বসিয়ে প্রসেশান করে চলেছে।
ব্যাপারটা শবযাত্রা না বিয়ে এই নিয়ে আমরা জল্পনা-কল্পনা করছি এমন সময়ে অ্যালাস্টার বলল যে আজ এখানে এক বিশেষ উৎসব।
কীসের উৎসব?
আমরা সমস্বরে শুধোলাম।
ও বলল—Dorffest.
সেটা আবার কী?
ও বলল, এল যে শীতের বেলা বরষ পরে। তাই এবার আল্পস পাহাড়ে যেসব গোরুদের গরমের সময়ে চরতে পাঠানো হয়েছিল, তাদের নেমে আসার পালা সমতল ভূমিতে। আজ সেই গোরুদের নেমে আসার উৎসব–অস্ট্রিয়ার এ এক ফেস্টিভ্যাল। গোরুরা হাত-পা না ভেঙে হাম্বা হাম্বা করতে করতে ফিরে আসুক-পেছন পেছন অ্যালসেশিয়ান কুকুরগুলোও ঘাউ ঘাউ করতে করতে–আজ সবাই তাই প্রার্থনা করে। প্রার্থনা করে, গোরুদের ভালো হোক, ওরা বেশি করে দুধ দিক।
মনে মনে বললাম, তবে রে, ব্যাটা ইষ্টুপিড; ইংরেজ! তোরা সারাজীবন আমাদের গোরু পুজোর খোঁটা দিয়ে এলি আর তোদের সব বাঘা বাঘা ভাই বিরাদররাও যে গোরু পুজো করে তার বেলা?
না কি স্যুট-পরা সাদা সাহেব, মার্সিডিজ গাড়ির বনেটে ফুলের তোড়া সাজালে পুজো হয় না, গোরুর পায়ে ভুড়িওয়ালা কালো পান্ডা গাঁদাফুল আর গঙ্গাজল দিলেই পুজো হয়!
সাহেবরাও যে গো-পুজো করে এটা জেনে রীতিমতো আত্মশ্লাঘা বোধ করলাম। পেছনে বসা নেতা সাহেবকে একথা বলে একের ক্ষীণকণ্ঠে যতটুকু ইংরেজের চরিত্রহনন করা যায় তাই-ই করতে সচেষ্ট হলাম।
বাস ততক্ষণে ব্রেনার পাসের দিকে অনেকখানি এগিয়ে গেছে। কিন্তু ওপাশ থেকে যত গাড়ি আসছে তাদের ছাদ বনেটে উইণ্ডস্ক্রিনে গুঁড়ো গুঁড়ো বরফ। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখি এবার যেসব গাড়ি আসছে তাদের ওপর গুঁড়ো গুঁড়ো নয় প্রায় তাল তাল বরফ।
তারপর ব্রেনার পাসের দিক থেকে আসা গাড়িগুলোকে আর দেখাই যাচ্ছিল না। শুধু সাদা বরফে ঢাকা। ওয়াইপার কোনোরকমে অতিকষ্টে বরফ সরাচ্ছে। দেখতে দেখতে আমরা বরফের রাজত্বে এসে পড়লাম। দু-পাশের মাঠঘাট ঘরবাড়ি সব বরফে ঢাকা। সে এক দারুণ অভিজ্ঞতা।
আমি বাঙাল তাই আমার কাছে বরফ পড়া দেখার অভিজ্ঞতা দারুণ। কিন্তু সাহেবদের কাছে এ তো রোজকার ঘটনা। আমার এই পরদেশে আসার উত্তেজনাকর পরদেশি এই অভিজ্ঞতার সঙ্গে স্বদেশি কোনো সমতুল অভিজ্ঞতার তুলনা করি এমন তুলনা মনে এল না।
পরক্ষণেই মনে পড়ল আমাদের কালবৈশাখী!
কলকাতার লোকের কাছে কালবৈশাখী কিছু নয় কিন্তু একজন অস্ট্রিয়ানের কাছে এ নিশ্চয়ই এক অভিজ্ঞতার মতো অভিজ্ঞতা। ধুলোর ঝড়, নারকোল গাছগুলোর মাথা নাড়ানো, মেঘের গুরু গুরু,আকাশের কালো কুটিল রূপ, বিদ্যুতের ঝিলিক; বাজের শব্দ।
কিছুদূর গিয়ে বাস আর যেতে পারল না। সামনে গাড়ির লাইন। দাঁড়িয়ে আছে। ব্রেনার পাসের দিকে আর কোনো গাড়ি যাচ্ছে না, মানে যেতে পারছে না। ওপাশ থেকে যেসব গাড়ি পাস পেরিয়ে ফেলেছে কোনোক্রমে, সেগুলোই তিরতির করে আস্তে আস্তে আসছে।
যে হারে বরফ পড়ছে তাতে মনে হল এখানেই এই বড়ো বাসটারই বুঝি বরফ-সমাধি হবে।
সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মোটরগাড়িগুলোর রং চেনার উপায় নেই। সব সাদা। আশেপাশের বাড়ি দোকান গাছ-পাতা সব সাদা। পুলিসম্যানের ওভারকোটের নীলচে রং সাদার মধ্যে থেকে একটু-একটু উঁকি মারার চেষ্টা করছে। টুপি সাদা।
বাস দাঁড়াল তো দাঁড়ালই।
অ্যালাস্টার ও জ্যাককে খুব চিন্তান্বিত হয়ে কী সব আলোচনা করতে দেখা গেল ফিসফিস করে।
ইতিমধ্যে আমাদের পেছনেও শয়ে শয়ে গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়েছে। জ্যাক নেমে পুলিশের সঙ্গে অনেকক্ষণ বুড়ো আঙুল কড়ে আঙুল, ডান হাঁটু নাড়িয়ে কথা বলল–তারপর বরফে ঢেকে গাড়িতে ফিরে এসে অ্যালাস্টারকে কী সব বলল বিজাতীয় ভাষায়।
অ্যালাস্টার মাইক্রোফোনে বলল, ওয়েল!
তারপর টিপিক্যাল ইংরেজের মতো ট্যাক্টফুলি একটু হাসল।
পরক্ষণেই বলল
Well, ladies and gentlemen, theres a minor problem!
হোয়াট ইজ ইট? হোয়াট ইজ ইট? রব উঠল।
আমার তিন সারি সামনে কানে-খাটো এক ফ্রেঞ্চ ভদ্রলোক ছিলেন, তাঁর নাম জানিনি। চেঁচিয়ে কথা বলার ভয়েই আলাপ করা হয়ে ওঠেনি। তবে মুখের ভাবটি সবসময়েই ভারি প্রশান্ত। তিনি তাড়াতাড়ি পকেট থেকে হিয়ারিং-এইড বের করে কানে লাগালেন।
পেছন দিক থেকে ইজরায়েলের সারা, ট্রিনিডাডের কালোজামের মতো পুরন্ত ঠোঁট-সম্পন্ন লুসি, সেই মালয়েশিয়ান দম্পতি, রয়্যাল এয়ার ফোর্সের গলায় স্কার্ফ বাঁধা চালু ভদ্রলোক, সেই পাসপোর্ট হারিয়ে যাওয়া ভদ্রমহিলা সকলেই একসঙ্গে ঔৎসুক্য প্রকাশ করলেন।
সব গলা ছাপিয়ে একটি বাঙালি গলা শোনা গেল; সেরেছে।
এই বাঙালি দম্পতি গ্রেটার লানডানে সেটলড। স্বামী এঞ্জিনিয়ার, স্ত্রী ডাক্তার। কিন্তু আমি বাঙালি পরিচয় দিইনি। আসা-ইস্তক একটি বাংলা শব্দও বলিনি। লোকে আমাকে যে যাই ভাবুক-পাকিস্তানি, আফ্রিকান, আরব, ইরানি,মেকসিকান, মাফিয়া আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি ছিল না।কিন্তু ক-দিনের জন্যে বিদেশ দেখতে এসে গড়িয়াহাটে কই মাছের দর অথবা অপর্ণা সেনের লেটেস্ট বাংলা ছবি নিয়ে আলোচনা করার একটুও ইচ্ছা আমার ছিল না। যদিও কই মাছ (বিশেষ করে ধনেপাতা ও সর্ষে-বাটা দিয়ে রান্না করা কই মাছ) এবং ওই বুদ্ধিমতী উজ্জ্বল চোখসম্পন্ন মহিলা–এই দুয়েরই আমি সবিশেষ ভক্ত।
অ্যালাস্টার আবার হাসল, যাকে চাকল করা বলে তেমন। তারপর মাইক্রোফোনে ফুঁ দিল। সম্মিলিত অভিব্যক্তি ধুলো ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেওয়ার জন্যে।
অ্যালাস্টারের চেহারা চুল কথাবার্তা সমস্তই অতিরোমান্টিক। বড়ো সুন্দর ছেলে। সে কারণেই ও প্রবলেমের খবর দেওয়া সত্ত্বেও আমাদের অতটা হতাশ হওয়ার কারণ আছে বলে মনে হল না।
অ্যালাস্টার বলল–আমাদের ইটালি যাওয়া বোধহয় হচ্ছে না।
আর যায় কোথায়? যেই না একথা বলা!
আমার মনে হল দিঘা বা বিষ্ণুপুরের কনডাকটেড ট্যুরে বেচারি ইনফরমেশন অ্যাসিস্ট্যান্টদের যাত্রীদের কাছ থেকে যে অভদ্র অবুঝ ও অশালীন ব্যবহারের সম্মুখীন হতে হয় তারই স্যাম্পেল দেখতে পাবে আজ অ্যালাস্টার।
হই হই রই রই রব উঠল। নেহাত সাহেব মেম ইংরিজিতেই কথা বলছিল–কিন্তু যা বলছিল তার অর্থ করলে অত্যন্ত সরল অর্থ দাঁড়ায়। দাও টাকা ফেরত, চালাকি পেয়েছ? বাপের নাম খগেন করে দেব। ভাঁওতা মারার জায়গা পাও না? কেস ঠুকে দেব বলে দিচ্ছি, দেখে নেব ইত্যাদি ইত্যাদি।
আবারো মনে হল সারাপৃথিবীর মানুষই এক। সেই মুহূর্তে মনে হল সাহেবরা দু-শো বছর আমাদের পরাধীন করে রেখে তাদের সম্বন্ধে যা আমাদের বুঝতে দেয়নি তা এই একমুহূর্তেই বোঝা গেল।
তার পা মাড়িয়ে দিলে, তার স্বার্থে, আরামে বা মানিব্যাগে হাত পড়লে পৃথিবীর সব মানুষই সমান।
আমি একবার চোখ ঘুরিয়ে এদিক ওদিক তাকালাম।
এই তিনদিনের ভদ্রতা সভ্যতা, থ্যাঙ্ক-ইউ, একসকিউজ মি ইত্যাদি যে কত বড়ো মুখোশ, কত বড়ড়া বাহ্য এবং মিথ্যা ব্যাপার তা আর জানতে বাকি রইল না।
বড়ো লজ্জা হল আমার। এদের সকলের জন্যে, আমার নিজের জন্যেও।
আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, অ্যালাস্টার তার কথা শেষ করেনি। তার অসুবিধের কথা তাকে দয়া করে বলতে দেওয়া হোক।
তক্ষুনি আমার পেছন থেকে আমাদের নেতা জন উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ইউ আর অ্যাবসোলিউটলি রাইট। লেট আস হিয়ার হোয়াট অ্যালাস্টার হ্যাজ টু সে। আফটার উই হিয়ার হিম উই উইল কাম টু আ ডিসিশান।
অ্যালাস্টার বলল, ব্রেনার পাস বরফে সম্পূর্ণ ঢেকে গেছে। কতক্ষণে বরফ পরিষ্কার করা যাবে, কতক্ষণে বরফপড়া থামবে–Its no-bodys guess
আসলে এ বছরে এত তাড়াতাড়ি যে বরফ পড়বে এবং এমনভাবে পড়বে–ব্রেনার পাসের তদারকি যাঁরা করেন তাঁরাও বুঝতে পারেননি।
সকলে সমস্বরে বলল, কী হবে? তাহলে কী হবে?
কেউ কেউ জুতো দিয়ে বাসের মেঝেতে পা ঠুকতে লাগল।
হংকং-এর চাইনিজ মেয়েগুলো বাসের একেবারে পেছন থেকে চ-কার এবং অনুস্বারের তুবড়ি ছোটাল।
অ্যালাস্টার বলল, ইটালিতে তো আমাদের হোটেল ঠিক করা আছে। ডিনারও সেখানে তৈরি করে রাখবে–কিন্তু এখন সারারাত এখানে আটকে থাকলে কী হবে? এটা একেবারে আনএক্সপেকটেড ব্যাপার। আমার কাছে পয়সাও নেই যে তোমাদের এত লোকের থাকা খাওয়ার বন্দোবস্ত করি এখানেই কোথাও।
অনেক স্বর একসঙ্গে বলল, চোপ। ইয়ার্কি পেয়েছ? পয়সা নেই মানে কী? কেন? তোমরা ক্রেডিটে বন্দোবস্ত করো–ওসব আমরা জানি না। আমরা ইটালি যাবই। এদিকে কোথাও খাওয়া-দাওয়া করে সারারাত বাস চালিয়ে চলো।
অ্যালাস্টার অভদ্র হয়ে-যাওয়া বিক্ষুব্ধ অতজনের সামনে হাসি-হাসি মুখে দাঁড়িয়ে রইল। যেন ও-ই সবকিছুর জন্যে দায়ী।
তখন জন উঠে দাঁড়িয়ে বলল–পাস পেরোবার কোনো উপায়ই কি নেই অ্যালাস্টার?
অ্যালাস্টার বলল-ব্রেনার পাসের নীচে দিয়ে একটা টানেল আছে–ট্রেনে করে গাড়ি পার হয়। শীতকালে যখন পাস বরফে ঢাকা থাকে। এখনও পার হচ্ছে অনেক গাড়ি কিন্তু এত বড়ো বাস তো ওই টানেল দিয়ে গলবে না।
জন শুধোল, আর কোনো উপায় নেই?
আছে। যদি টায়ারে স্নো-চেইন লাগানো যায়।
তোমাদের সঙ্গে আছে? জন শুধোল।
জ্যাক বলল, এই সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি যে এমন বরফ পাব এখানে কে জানত? নেই! আমাদের সঙ্গে চেইন নেই!
অ্যালাস্টার তুড়ি মেরে বলল, নট আ ব্যাড আইডিয়া; উই ক্যান ট্রাই দ্যাট আউট।
তারপর রয়্যাল এয়ার ফোর্সের সাহেব, জন, অ্যালাস্টার ও জ্যাক চেইন পাওয়া যায় কি না খোঁজ করতে বেরোল।
আমার পাশের ফিলিপিনো ভদ্রমহিলা ব্যাগ থেকে একগাদা বিস্কুট ও চকোলেট বের করে দিলেন। উনি বড়োলোক। আমার এদেশে বাড়তি চকোলেট বা বাড়তি খরচ করারও টাকা নেই।
খিদেও পেয়েছিল। বিকেলে চা-ও খাওয়া হয়নি, এদিকে রাত নেমে এল বলে। বহু বহু বছর বাদে কুটমুট করে বিস্কুট চকোলেট খেলাম–
কিণ্ডারগার্টেনে পড়া ছেলের মতো।
ওরা ফিরে এল।
বলল, কোথাও চেইন পাওয়া গেল না।
অ্যালাস্টার ব্রাসেলস-এ কসমস কোম্পানির হেড কোয়ার্টারে ফোন করতে চেষ্টা করল একটা দোকান থেকে। ব্রাসেলস-এর বস-এর সেক্রেটারি বলল যে তিনি অফিস থেকে বেরিয়ে এক পার্টিতে গেছেন।
জনের ভগ্নীপতি যে ভারতবর্ষে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এসেছিল, মুঠি পাকিয়ে বলল–টু হেল উইথ দ্য পার্টি।
জন বলল, যা হয় একটা ঠিক করা হোক। বাস থেমে থাকলে তো আর ব্রোয়ার চলবে না সারারাত–আমরা কি এই ব্রেনার পাসের ওপরে ঠাণ্ডায় জমে মারা যাব?
আর এ এফ-এর সাহেব বলল, মেয়েদের খুব খিদে পেয়েছে, কেউ চা পর্যন্ত খায়নি বিকেলে, বাসটাকে কোনোক্রমে পাশের গলিতে ঢুকিয়ে একটা চায়ের দোকানের সামনে অন্তত আপাতত নিয়ে যাওয়া যাক।
ইংরেজ পুরুষগুলো ভারি সেয়ানা। যা-কিছু দয়া-ফয়া, ফেভার-টেভার চায় সব মেয়েদের নাম করে।
বাস থেকে আমি একবার নেমেছিলাম, একটু বরফের ওপর হাঁটার শখ হয়েছিল। প্রচন্ড ঠাণ্ডা। একটুক্ষণ পরই আবার বাসের গরমে ফিরে আসতে বাধ্য হলাম।
জন, এয়ার ফোর্সের সাহেব এবং আমি মিলে আলোচনা করে ঠিক করা হল, সারাদিনের যাত্রার পর আবার সারারাত বাস চালিয়ে গিয়ে ইটালি পৌঁছোনার চেষ্টা করাটা খুবই ঝুঁকি নেওয়া হবে।
জন বলল, তা ছাড়া জ্যাক সারাদিনে আইনমাফিক যতখানি চালানো সম্ভব প্রায় চালিয়েছে। এরপর সারারাত চালানো বেআইনি হবে।
আমার জানা ছিল না যে এরকম আইন কোথাও আছে। আছে জেনে ভালো লাগল।
জ্যাক বাসটা ব্যাক করে নিয়ে পাশের গলিতে ঢুকল। সেখানে পর পর অনেকগুলো দোকান, রেস্তোরাঁ।
অ্যালাস্টার বলল, আপনারা চা-টা খেয়ে নিন এখানে। আমি ততক্ষণে ব্রাসেলসে আবার ফোন করে দেখি, যোগাযোগ করতে পারি কি না।
আগেই বলেছি, পশ্চিমি দেশে ফোনে এ-প্রান্ত থেকেও-প্রান্ত অবধি যোগাযোগ করাটা কোনো ব্যাপারই নয়। এরিয়াকোড় ঘুরিয়ে নাম্বার ডায়াল করলেই হল। ডায়রেক্ট ডায়ালিং পৃথিবীর এদিকে সর্বত্র! এখন কসমস কোম্পানির ইয়োরোপিয়ান বস যেখানে পার্টিতে গেছেন সেখানকার ফোন নম্বর পেলেই ঝামেলা মিটে যায়।
বাইরে তখন বরফ পড়া থেমে গেছে, কিন্তু টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ হয়েছে।
বাস থেকে নামতেই মনে হল ঠাণ্ডায় কে যেন কান কেটে নিয়ে গেল। নেমেই, সামনে দেখি একটা বার ও রেস্তোরাঁ। প্রায় সাতটা বাজে। অন্যান্য দিন এমন সময়ে আমরা ডিনারে বসে যাই। খিদেও পেয়েছে।
বার-এ সার সার ওয়াইন, লিকার, হুইস্কি, শ্যাম্পেন ইত্যাদির বোতল সাজানো আছে। হঠাৎ একটু বড়োলোকি করে গরম হওয়ার ইচ্ছে গেল। এমন সময়ে দেখি, আমার পেছনে সারা। জিনের ফ্লেয়ার, জিনের শার্ট আর তার ওপরে একটা বুক-খোলা হাতওয়ালা সোয়েটার পরে। বাস থেকে নেমেই অবশ্য সোয়েটারের সবকটা বোতাম বন্ধ করে নিয়েছে।
সারা বলল, হাই।
আমি বললাম, হাই!
বাস থেকে নেমে এটুকু এসেই মেয়েটার ঠোঁট নীল হয়ে গেছে ঠাণ্ডায়।
বললাম, কেয়ার ফর আ ড্রিঙ্ক?
সারা আমার দিকে তাকাল, তারপর স্বল্পপরিচিত আমার দিকে তাকিয়ে বলল, আই উডনট মাইণ্ড।
আমি বললাম, কী খাবে?
ও বলল, কনিয়াক।
আমরা দুটো কনিয়াক নিলাম।
এখন ডিনারের ব্রেক নয়। তা ছাড়া পয়সা যখন দিয়েছে ট্যুর কোম্পানিকে তখন খিদে পেলেও নিজের পয়সায় ডিনার খাবে এমন ইচ্ছা কারোরই দেখা গেল না। এমতাবস্থায় গরিব ইণ্ডিয়ানের পক্ষে কপির স্যুপ এবং আলু-মটরশুটি সেদ্ধ খাওয়াটাও বড়োলোকি বলে গণ্য হবে হয়তো। তা ছাড়া সবাইকে ফেলে একা একা খাওয়াটা অশোভনও বটে। কনিয়াকটা শেষ করতে না করতে অ্যালাস্টার এসে খবর দিল যে, যোগাযোগ করা যায়নি; কিন্তু জোর চেষ্টা চলছে। অতএব আমি আর সারা আরও একটা করে কনিয়াক গিলে বাসে ফিরে এলাম। অন্যান্যরা কেউ চা, কেউ কফি, কেউ টকাস করে একটু স্ন্যাপস খেয়ে বাসে ফিরে এসেছেন।
বাইরে বৃষ্টি জোর হয়েছে। বাসের কাঁচে পিটির পিটির করে ছাঁট লাগছে। ব্লোয়ারটা দাঁড়ানো অবস্থায় অনেকক্ষণ চলেছে বলে জ্যাক বন্ধ করে দিয়েছে এখন। নেতা জনের নির্দেশে। বেশ ঠাণ্ডা লাগছে। কোটের কলার তুলে, হাত পকেটে ভরে হেলান দিয়ে বসে আছি। বাইরে রাত নেমে এসেছে। কাঁচে বৃষ্টির জল পড়ায় বাইরে বিশেষ কিছু দেখা যায় না। বরফের সাদা, প্রতিফলিত আলো; বড়োরাস্তায় ভিড় করে থাকা গাড়িগুলো সব মিলিয়ে মাথার মধ্যে এক অসংলগ্ন ভাবনার ট্রেন চলেছে ধীরে ধীরে ক্লান্তির টানেলের মধ্যে দিয়ে।
হঠাৎ জনের শালা বলে উঠল–লুক জন। আই টোল্ড উ্য জার্মানি উইল ফাইন্যালি গেট আস।
আমি হেসে উঠলাম।
জনও হেসে উঠল। অন্য অনেকেই হাসলেন।
জন আমাকে বলল–দিস ব্লাইটার অফ আ ব্রাদার-ইন-ল কান্ট ফরগেট হিজ ইয়ারস ইন দ্য ওয়ার।
রসবোধ আছে শালাবাবুর। যুদ্ধের সময়ে হেলমেট মাথায় দিয়ে চুইংগাম চিবোতে চিবোতে হাওয়াইটজারের আলোয় আলোকিত আকাশে তাকিয়ে ভয়ার্ত গলায় এই কথাই অনেকবার মনে মনে বলেছে বাবু। আজ জার্মানিতে সত্যি বার্ধক্য ও অসহয়াতার বলি হয়ে তাই বুঝি পুরোনো কথাটা মনে পড়ে গেছে এমন করে।
মেয়েরা অনেকে ঘুমোচ্ছেন। পিছনের সিটে এয়ারফোর্সের পাপা তার পাতানো মেয়েদের সঙ্গে সমানে বকে চলেছে। যুবতী মেয়েগুলো একগামলা কইমাছের মতো খলবল খলবল করছে। চাইনিজ, ইজরায়েলি, মালয়েশিয়ান, কেনিয়ান, অস্ট্রেলিয়ান–একগাদা মেয়ে একসঙ্গে কথা বললে ঠিক জলতরঙ্গের মতো আওয়াজ হয়।
এমন সময়ে জ্যাক তড়াক করে দরজা খুলে ভেতরে এসে মহাসমারোহে বাও করে বলল –প্রবলেম–ফিনি…।
জ্যাক ইংরিজির মধ্যে থ্যাঙ্ক ঊ্য; প্রবেলেম; নো প্রবলেম; গুড; ব্যাড এবং মাদাম; মিস্টার এই কটা কথা জানত। কিন্তু এই সামান্য ক-টি কথা সম্বল করে চোখ-মুখের অভিব্যক্তি দিয়ে সে যেভাবে কথা বলত বহু ভাষাভাষী সর্বজ্ঞ হয়েও তেমন করে বলা যায় না।
সকলে আনন্দে হই হই করে উঠলেন। শীতের লম্বা রাত অভুক্ত শয্যাহীন অবস্থায় কী করে কাটানো হবে এই চিন্তা সকলকেই কম বেশি পেয়ে বসেছিল। এমন সময়ে অ্যাযুলাস্টার এল।
মাইক্রোফোনে বলল, ব্রাসেলসের সঙ্গে কথা হল। এ যাত্রা আমাদের ইটালি যাওয়া হবে না। আমরা আবার কেম্পটেনে ফিরে যেখানে দুপুরে খেয়েছিলাম–সেই অস্ট্রিয়ান হোটেলওয়ালার সুন্দরী ইংরেজ স্ত্রীর হেপাজতে ফিরে যাব। ওখানেই খাওয়া-দাওয়া করে দু তিনটে হোটেলে ভাগ করে শুয়ে পড়ব। সকালবেলা ব্রেকফাস্টের পরে দশটা নাগাদ কনফারেন্স করে পরবর্তী গন্তব্য ঠিক করে নিয়ে আবার পথ চলা শুরু হবে।
জ্যাক বাসটা স্টার্ট করল। আবার ব্লোয়ার চলতে শুরু করল। বাসটা মুখ ফেরাল কেম্পটনের দিকে।
বেশ ক-দিন পর সকাল ন-টা অবধি পালকের লেপ গায়ে দিয়ে ঘুমোনো যাবে যে, একথা ভেবেই আরামে আমার ঘুম পেয়ে গেল। বাস চলতে লাগল হু-হু করে। ভেতরের বাতি নিবিয়ে নাইট লাইট জ্বালিয়ে দিল অ্যালাস্টার। ভোর ছটায় চলা শুরু হয়েছে আর এখন রাত প্রায় সাড়ে নটা। কারোরই আর জেগে থাকার ইচ্ছা বা জোর ছিল না।
পুরো বাসে বোধহয় ড্রাইভার জ্যাক, গাইড অ্যালাস্টার, নেতা জন এবং আমিই জেগে রইলাম।
সকলে যখন যা করে আমার তখন ঠিক তার উলটোটা করতে ইচ্ছে করে চিরদিন। বরফ ঝরা নির্জন হিমেল রাতের জার্মানির গ্রামের রূপে চোখ ডুবিয়ে বসে রইলাম।
সকালে বলাবাহুল্য আমার উঠতে দেরি হয়েছিল।
ব্রেকফাস্ট করে বাইরে এসে দেখি ঝকঝকে রোদ। চারদিকে বৃষ্টিস্নাত ঘরবাড়ি পথঘাট– চমৎকার দেখাচ্ছে।
কনফারেন্স যত সহজে শেষ হবে ভাবা গেছিল তত সহজে হল না। প্রবল আপত্তি উঠল নানাতরফ থেকে। নানা মুনির নানা মত। অনেকেই জ্যাক ও অ্যালাস্টারের সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করতে লাগল। যেন ওরাই ব্রেনার পাসের ওপর নিজে হাতে গামলা গামলা বরফ ঢেলে আমাদের ইটালি যাওয়া ভন্ডুল করেছে।
আগেই বলেছি, জনগণ সর্বত্র এক। পাঁচমিশেলি লোকে ভরা। নয়াপয়সা দিয়ে টাকা উসুল করার মনোবৃত্তিটা শুধু আমাদেরই একচেটিয়া নয় দেখে মনে মনে আত্মশ্লাঘা বোধ করলাম।
শেষে মেজরিটির ডিসিশান মানতেই হল। অবশ্য এই ডিসিশান মানাতে জন এবং আমার অনেক মেহনত করতে হল। সেই মুহূর্তে আমাদের সেই গোল হয়ে দাঁড়ানো কনফারেন্স দেখলে যে-কেউ মনে করতে পারত যে এর মধ্যে স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস এবং গান্ধিজিও আছেন;
উত্তেজনা প্রশমিত হলে বাস ছাড়ল জ্যাক।
বাঁ-হাতের পাঁচ আঙুল তুলে আমাদের দিকে দেখিয়ে বলল, নো প্রবলেম।
দেখতে দেখতে আমরা অস্ট্রিয়ার বিখ্যাত টীরল প্রভিন্সে এসে পৌঁছোলাম। এই প্রদেশের নামেই লানডানের বেইজওয়াটার স্ট্রিটের সেই অস্ট্রিয়ান রেস্তোরাঁ টীরলার হুট। যার কথা আগে বলেছি। পথের দৃশ্য যে কী সুন্দর তা বলার নয়। চতুর্দিকে বরফ বরফ পাহাড়গুলো পা অবধি বরফে ঢাকা-উপত্যকা-গাছপালা-পথের পাশের সব কিছু বরফে ঢাকা। সব সাদা। রাতে বরফ পড়েছে–এখন আস্তে আস্তে গলে যাচ্ছে। অটোবান দিয়ে এত জোর ও এত বেশি সংখ্যক গাড়ি যায় সব সময়ে যে, পথটা ভিজে থাকার অবকাশ পায় না–গাড়ির চাকায় চাকায় শুকিয়ে যায় নিমেষে।
ডান দিক দিয়ে ইন নদী বয়ে চলেছে পথের পাশে পাশে। ভারি সুন্দরী ছিপছিপে নদী। অনেকটা আসামের ও ভূটানের সীমানার যমদুয়ারের কাছের সংকোশ নদীর মতো।
যেখানে বরফ পড়ে নেই সেখানের দৃশ্য যেন আরও সুন্দর। কী যে নয়নভোলানো সবুজ, তা বলার নয়। চতুর্দিকে আল্পস-এর বরফাবৃত শ্রেণি।
আসটাগ বলে একটা গ্রামের পাঁচতলা হোটেলে আমরা দুপুরের খাওয়া খেলাম। কাছেই স্কি-লিফট ও স্কি-ক্লাব আছে অনেক। হোটেলটার মধ্যে সনা বাথ, হিটেড সুইমিং পুল সব আছে। আশেপাশে কাছাকাছি কোনো শহর নেই। এখনও এখানে ভিড় তেমন জমেনি– কারণ স্কিইং-এর সময় এখনও শুরু হয়নি এখানে। বরফ এখন এখানে যা পড়েছে তা স্কিইং করার উপযুক্ত নয়। কিন্তু তবুও কিছু কিছু অত্যুৎসাহী লোক এসে জড়ো হচ্ছে। নারী-পুরুষ মাউন্টেনিয়ারিং-এর উজ্জ্বল লাল-নীল পোশাক পরে হেঁটে বেড়াচ্ছে জোড়ায় জোড়ায়।
দুপুরের খাওয়া সেরে ভারি সুন্দর পথ বেয়ে মাইল চল্লিশেক এসে একটা ছোটো স্কিইং ভিলেজের ছিমছাম হোটেলে উঠলাম। গ্রামটা ইনসব্রাক-এর পথে পড়ে।
বিকেলে খটখটে রোদ থাকতে থাকতে হাঁটতে বেরিয়েছিলাম। তখনও ওভারকোট পরে যেতে হল এত ঠাণ্ডা। বিকেলেই চার ডিগ্রি ফারেনহাইট। রাতে শূন্যের নীচে চলে যায় তাপাঙ্ক। এই শুকনো রৌদ্রালোকিত ঠাণ্ডায় নিশ্বাস নিতে ভালো লাগে। মনে হয় বুকের কলজে বিলকুল সাফ হয়ে গেল।
চতুর্দিকে বরফ-ঢাকা পাহাড়; নীল আকাশ। আল্পসের চুড়ো বরফে বরফে সাদা হয়ে আছে। চুড়োর নীচে কালো জঙ্গল। বেশির ভাগই পাইন আর ফার। ছবির মতো। কিন্তু এদেশে জঙ্গল পাহাড় ছবিরই মতো। আমাদের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে যে আদিমতা, রসহ্যময়তা তা এদের নেই। বড়োলোকের নিখুঁত সুন্দরী মেয়েদের মতো এই সৌন্দর্য এত বেশি ভালো যে তাকে ভালো লাগাতে ইচ্ছা করে না।
আজ দুপুরে যখন অস্টিগে খাওয়ার জন্যে দাঁড়িয়েছিলাম তখন শিঙে বাজিয়ে পাহাড়ের ওপর থেকে গোরু-চরানো রাখাল ছেলেদের ডাকছিল সমতলের লোকেরা–লাঞ্চ খেতে আসার জন্যে। গোরুর গলার ঘণ্টা আমাদের দেশের গোরুর গলার ঘণ্টার মতোই। পেতলের; মিষ্টি অথচ গম্ভীর আওয়াজ। অস্ট্রিয়ায় গোরুর গলার ঘণ্টা বাজিয়ে সাধারণ লোকেরা নানারকম গান-বাজনা করে। নাচেও। রাখাল ছেলেদের আগে আগে বড়ো বড়ো শেফার্ড ডগ কুকুরগুলো গোরুদের সঙ্গে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে গম্ভীর ঘাউ ঘাউ ডাকে পাহাড়তলি মুখরিত করে নেমে আসছিল।
হাঁটতে হাঁটতে একটা স্কিইং ক্লাবের চৌহদ্দির মধ্যে পৌঁছে গেলাম। একটা পাহাড়ের মাথা সমান করে সেখানে ক্লাব হাউস। এখন নিস্তব্ধ পড়ে আছে। বরফ ভালো করে পড়লে এই জায়গা লাল-নীল হলুদ পেশাকে-সাজা স্কিইং রসিকদের ভিড়ে ভরে যাবে। স্কি-লিফট চলে গেছে পাহাড়ের নীচ থেকে ওপরে–এ-পাহাড়ের নীচ থেকে ও-পাহাড়ে। লিফট মানে কেবল-কার। কেবল-কারে পাহাড়ের চুড়োয় পৌঁছে সেখান থেকে স্কিইং করে নেমে আসে নীচে। আশে-পাশে রেস্তোরাঁ, বার, কীয়সক; লগ-কেবিন, ছড়ানো-ছিটানো থাকে।
অটোবান দিয়ে সোঁ-সোঁ করে গাড়ি চলেছে। যেসব জায়গায় গাড়ি চলে সেখানে হাঁটা নিরাপদ নয়। হয়তো বেআইনিও। রাস্তা পার হওয়াও বিপদজ্জনক। দূর থেকে দেখা যাচ্ছে একটা গাড়িকে স্থির বিন্দুর মতো কিন্তু রাস্তা পেরুতে না পেরুতেই গাড়িটা কাছে এসে পড়ল। আসলে, এত বেগে গাড়ি চলে এখানে যে, আমাদের গতির অভিজ্ঞতার সঙ্গে মেলে না। সে কারণে আন্দাজে ভুল হয়ে যায়।
হেঁটে ফিরে এসে চা খেলাম এককাপ। আটটি অস্ট্রিয়ান শিলিং নিল। ইনকিপারকে দেখতে জব্বর। অস্ট্রিয়ান কাউন্টের মতো। কাউন্ট অব শ্যাটোনোয়ার মতো চেহারা। ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি –সাড়ে ছ-ফিট লম্বা। তাঁর স্ত্রী কিচেন ও অফিস সামলায়। সার্ভ করে বাবা ও ফুটফুটে মেয়ে।
চা খেয়ে লবিতে এসেছি এমন সময়ে সেই বাঙালি দম্পতির একেবারে মুখোমুখি। ভদ্রমহিলা সোজা আমার চোখে তাকালেন। তারপর চোখ থেকে চোখ না সরিয়েই বললেন স্পষ্ট বাংলায়, আপনি বাঙালি?
ভদ্রমহিলার আন্তরিক স্বরে প্রবাসে চমকে উঠলাম।
ছাত্রাবস্থায় অনেক শখের অভিনয় করেছিলাম। তারপর জীবনের পরীক্ষায় নেমে প্রায়ই প্রয়োজনের অভিনয় করে করে শখের অভিনয় কাকে বলে তা ভুলে গেছিলাম। তবুও ভাবলাম বলি, চোস্ত ইংরিজিতে যে আমি ইরানের লোক।
কিন্তু পারলাম না। হেসে ফেললাম।
হাসিটা বেধহয় আধেক ধরা পড়েছি গো আধেক আছে বাকির মতো মনে হল ওঁর কাছে।
তিনি বললেন রাগত স্বরে, আপনি খুব অসভ্য! এত দিন হয়ে গেল এমন লুকিয়ে রাখলেন আপনার বাঙালি পরিচয়?
তারপই বললেন, কিন্তু কেন?
আমি হাসলাম, বললাম, কোনো কারণ ছিল না। এমনিই।
মিথ্যে কথা বললাম।
ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হল। মিস্টার ও মিসেস বোস। আগেই বলেছি, একজন এঞ্জিনিয়ার আর একজন ডাক্তার। কিন্তু একজন লানডানে থাকেন অন্যজন লানডান থেকে প্রায় দেড়শো মাইল দূরে–চাকরি ব্যপদেশে।
এই কন্টিনেন্টের ছুটি ওঁদের কাছে দ্বিগুণ আকর্ষণের। প্রথমত দেশ বেড়ানো; দ্বিতীয়ত কাছে কাছে থাকা।
পরে জেনেছিলাম মানে বুঝেছিলাম যে, আমার এই বাঙালি সহযাত্রীরা বর্তমান থাকতেও ভিনদেশিদের সঙ্গে এত বেশি মাখামাখি, ছেলে-মেয়ে নির্বিশেষে এমন অবাধ মেলামেশা ওঁদের রক্ষণশীল চোখে ভালো ঠেকেনি। কিন্তু আমি যে এরকমই। ছেলেবেলা থেকেই ঠাকুমা পিসিমা এমনকী মা-বাবারও কোনো প্রাকুটি আমার স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাচারিতাকে রোধ করতে পারেনি। অবশ্য তার দাম দিতে হয়েছে বুকের পাঁজর দিয়ে। কিন্তু এই মূল্যবান ও মাল্যবান স্বাধীনতারও একটা দাম আছে। কিছু না হারিয়ে যে এ জীবনে কিছুমাত্রই পাওয়া যায় না। পাওয়া গেলেও যে তা ছাগলের দুধ খাওয়া স্বাধীনতার মতোই জোলো প্রতিপন্ন হয় সে সম্বন্ধেও আমার বিশ্বাস দৃঢ় ছিল চিরদিনই।
যাই-ই হোক ওঁরা দুজনে বিশেষ করে মিসেস বোস আমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুবই খুশি হলেন। মিসেস বোসের স্বভাবটি ভারি সহজ সরল ও সুন্দর। মি: বোস গম্ভীর, সন্দিগ্ধ; ও কিঞ্চিৎ ঈর্ষাকাতর। স্ত্রী যদি স্বামীর সামনে অন্য পুরুষের প্রতি প্রয়োজনের তুলনায় বেশি ভালো ব্যবহার করেন সেখানে বাঙালি স্বামীমাত্ররই ঈর্ষা হয়ে থাকে। তার ওপর মিসেস বোসের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আছে–সুতরাং তাঁর স্বাধীনতাটাকে না মেনেও উপায় ছিল না। ভবিষ্যৎ ভেবে আমি সেই মুহূর্ত থেকেই একটু গুটিয়ে নিলাম নিজেকে। সংসারে সুখ বড়ো তরল জিনিস। নিজের পাত্র পূর্ণ থাকা সত্ত্বেও উপচে পড়া সুখ যদি অন্য পাত্রে গিয়ে পৌঁছোয় তাহলেও আমাদের সাধারণ রক্ষণশীল মানসিকতায় তা অসহ্য বলে মনে হয়। মি. বোসের দোষ নেই। আমারও নেই।
কিন্তু আমি অন্য কারও জীবনেই দুঃখ বা বিষণ্ণতা ইচ্ছে করে আনতে চাইনি কখনো। জীবনের অভিজ্ঞতার পাতা ভরে উঠেছে ভুল-বোঝাবুঝির কালো কালিতে। ঘর-পোড়া গরু তাই আকাশে সিঁদুরে মেঘ দেখলেই ভয় পেয়ে শিং নাড়ায়।
লবিতে বসে ম্যাগাজিনের পাতা উলটে গল্প করে, দেখতে দেখতে ডিনারের সময় হয়ে এল।
ডিনার সার্ভ করছিল ইনকিপার ও তার মেয়ে। এখন একটা সবুজের ওপর সাদা পোলকা ডটের কাজ-করা ওয়েস্ট কোট পরেছে হোটেল মালিক। তার দুধসাদা রং খয়েরি ফ্রেঞ্চ-কাট দাড়ি, দীর্ঘ সুগঠিত চেহারা দেখে আমি স্তুতিতে নির্বাক হয়ে গেলাম। স্যুপ ঠাণ্ডা হয়ে যেতে লাগল। খাওয়া ভুলে গেলাম। মেয়েটি হরিণীর মতো লঘু পায়ে একটি সাদা অ্যাপ্রন পরে সার্ভ করছিল। হাসি মুখ। বাবা ও মেয়ের মুখে কথা নেই।
ডাইনিং রুমের সার্ভিস কাউন্টারে কাঁচের ডিকান্টারে বুড়বুড়ি তুলে অ্যাপল জুস তৈরি হচ্ছে অনবরত।
দেখতে দেখতে খাওয়া শেষ হল।
এদিকে আমাদের সুন্দরী অস্ট্রেলিয়ান সঙ্গিনীরা এখনও ফেরেনি। ক্যারল ও জেনি আজ রাতে ফিরে আসবে ন্যুনিক থেকে তাদের বয়ফ্রেণ্ডদের সঙ্গে। কাল থেকে তারা আমাদের সঙ্গে থাকবে।
এই হোটেলের পাশেই একটা জায়গায় ডিসকোথেক ডান্স ও গেমস-এর জায়গা ছিল। ডিনারের পর প্রায় সকলেই সেখানে চলে গেল। এই রেকর্ডের সঙ্গে নাচ বা নানারকম বালখিল্য খেলায় আমার কখনো উৎসাহ ছিল না। বিদেশি নাচ সে ওয়ালটজ বা যে নাচই হোক না কেন বিদেশি যখন নাচে তখন দেখতে ভালো। কিন্তু আমাদের দিশি সাহেব মেমদের দেশ স্বাধীন হওয়ার এতদিন পরেও বিদেশিদের অন্ধ অনুকরণে ধেই ধেই নৃত্য দেখে আমার আজকাল নাচের কথা শুনলেই বমি পায়।
ক্লাবে, পার্টিতে ও অন্যান্য জায়গায় যখন পার্শে মাছের মতো মহিলারা কাৎলা মাছের মতো দিশি সাহেবদের সঙ্গে নাচেন তখন সেখানে বসে থাকতেও আমার অস্বস্তি লাগে। মনে হয়, সঙ্গ সুখের আরও তো অনেক উৎকৃষ্ট পথ আছে, তবুও এই নাচ কেন?
যে-কথা পরাধীনতার কালিমামময় বছরগুলোতে আমরা বুঝেছিলাম, বুঝেছিলাম ইংরেজদের পরমগৌরবময় অধ্যায়ে, যে যুগে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য কখনো অস্তমিত হত না সেই যুগে, সেকথাটাই আজ আমাদের নিজের দেশ নিয়ে গর্বের অনেক কিছু থাকা সত্ত্বেও, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য পরনির্ভর গরিব ও কাঙাল হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও আমরা ভুলে গিয়ে কত গর্ববোধ করি!
আমাদের মতো আত্মবিস্মৃত জাত বোধ হয় আর হয় না।
আজকে আমাদের ছেলে-মেয়েরা, বড়ো হয়, ন্যক্কারজনক ইঙ্গ-ভারতীয় খিচুড়িমার্কা কিণ্ডারগার্টেন স্কুলে পড়াশুনো শিখে। তারা আজ আর এক্কাদোক্কা খেলে না, বাংলা ছড়া বলে না, শিশু ভোলানাথ পড়ে না, তারা রিঙ্গা-রিঙ্গা রোজেজ, পকেটফুল অফ পোজেজ গান গাইতে শেখে–অ আ ক খ শেখার আগেই। ঠাকুরমার ঝুলি বা পথের পাঁচালি পড়ার আগেই তারা ইংরিজি কমিকস পড়া শেখে। স্বদেশেও একে অন্যকে হাই বলে সম্বোধন করে। রবিশঙ্কর বা ভীমসেন যোশীর বাজনা বা গান না শুনে তারা বিদেশি পপ মিউজিকের রেকর্ড শোনে।
দিনের পর দিন এসব দেখে শুনে আজকাল এক অসহায় বিষণ্ণতা আমাকে ছেয়ে থাকে। সবসময়ে। পাতাল রেল হওয়া সত্ত্বেও, আমরা অ্যাটম বোমা বানানো সত্ত্বেও, এত এত কলকারখানা, যন্ত্রপাতি, বাঁধ, রাস্তা বানানো সত্ত্বেও এই সমস্ত কিছুর সমস্ত গর্ব ছাপিয়ে আমাদের নিজস্ব সাহিত্য সংগীত সংস্কৃতিকে ভুলে যাওয়ার লজ্জাকর মনোবৃত্তির, এই আশ্চর্য হীনমন্যতার, এই কৃতঘ্নতার গ্লানি আমাকে সবসময়ে আচ্ছন্ন করে থাকে।
ওরা ওরা; আমরা আমরা। ওদের অনেক গুণ; দোষও অনেক। আমরা কেন আমাদের দোষ ও গুণ নিয়ে, আমাদের সাহিত্য, সংগীত ও সংস্কৃতি নিয়ে আমাদের ভারতীয়ত্বতে গর্বিত হতে পারি না আজকেও? একথা ভেবে বড়োই পীড়িত বোধ করি।
আমাদের নিজেদের যা আছে, তাকে সম্যকভাবে না হলেও, মোটামুটি জেনে তারপর পরের সংস্কৃতির খোঁজখবর রাখাটা বুদ্ধিমানের, সংস্কৃতিসম্পন্নতার লক্ষণ সন্দেহ নেই। কিন্তু নিজেদের আলমারির মধ্যে রাখা দামি বেনারসি বা আতরদানির খোঁজ না রেখে আমরা পরের দেশের ম্যাকসি ও ইন্টিমেন্ট সেন্ট নিয়ে মাতামাতি করি।
আমার দৃঢ়বিশ্বাস যে, যতদিন এই হীনমন্য প্রজাসুলভ অনুকরণপ্রিয় মানসিকতা আমরা কাটিয়ে না উঠতে পারব ততদিন আমাদের তাবৎ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার দাম কানাকড়িও নয়। এমার্জেন্সি ঘোষণা হওয়ায় স্বাধীনতা গেল গেল বলে আমরা চেঁচাই–অথচ স্বাধীনতা বলতে কী যে বোঝায় তার ন্যূনতম বোধও আমাদের অনেকের মধ্যে নেই। স্বাধীনতা কেউ কাউকে ঝিনুকে করে গিলিয়ে দিতে পারে না, তা যে অর্জন করতে হয়।
এসব ভাবলে উত্তেজিত বোধ করি, রক্তচাপ কমে যায়, মাথা ঘোরে কিন্তু আমার এই দুর্বল কলমে এই লজ্জাকর মনোবৃত্তির অবসান ঘটবে এমন মনে করার কোনো কারণ দেখি না। অনেকেই যদি এইরকম ভাবেন, অন্য দশজনকে আমাদের ভারতীয়ত্বে গর্বিত ও ন্যায্য কারণে স্পর্ধিত করে তুলতে পারেন তাহলে বোধহয় এই সর্বগ্রাসী অশিক্ষাপ্রসূত হীনমন্যতার অবসান হবে।
কোন কথা বলতে বসে কোন কথায় এলাম!
লবিটা এখন ফাঁকা। বুড়ো-বুড়িরা গিয়ে অনেকে শুয়ে পড়েছেন। কাল ভোর পাঁচটায় উঠতে হবে। কাল আমরা ইনসব্রাকে যাব। যেখানে উনিশো পঁচাত্তরের স্কিইং অলিম্পক।
হঠাৎ দেখি ইনকিপারের মেয়ে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল–জুতো হাতে করে।
বাবা-মা যাতে কাঠের মেঝেয় জুতোর শব্দ না শুনতে পান, সেজন্যে কি?
কে বলবে যে এই মেয়েই একটু আগে পরিবেশন করছিল। একটা পিংক গাউন পরেছে, চুলটা আঁচড়েছে ভালো করে, মুখে হালকা প্রসাধন; সেও চলেছে নাচতে। কার সঙ্গে কে জানে?
অ্যালাস্টার আমার পাশে বসেছিল।
মেয়েটি অ্যালাস্টারকে ফিসফিস করে বলল, ওন্ট উ্য?
অ্যালাস্টার বড়ো লাজুক। ভারি মিষ্টি ছেলে। ওর ট্যুরিস্ট গাইড না হয়ে অধ্যাপক হওয়া উচিত ছিল। হবেও হয়তো কোনোদিন। ইতিমধ্যেই পাঁচটি ভাষায় ওর সমান দখল।
লাজুক মুখে ও বলল, নো, থ্যাঙ্ক ঊ্য।
মেয়েটি অবাক হল। ওর এই প্রস্ফুটিত প্রথম যৌবনের গোলাপি অধ্যায়ে নাচের নিমন্ত্রণে এই বোধহয় ও প্রথম প্রত্যাখাত হল। মুখটা কালো হয়ে গেল বেচারির।
কথা না বলে দরজা খুলে পথে বেরিয়ে গেল।
জ্যাক একটু পর ঘরে ঢুকল, ও লা-লা-লা করতে করতে। আমাকে বলল, নো ম্যাডাম? প্রবলেম?
আগেই বলেছি, জ্যাকের ইংরিজি জ্ঞানের কথা। কিন্তু মুখে হাসি থাকলে এবং সকলের প্রতি ভালোবাসা ও সহানুভূতি থাকলে ভাষার বোধ হয় তেমন প্রয়োজন হয় না।
জ্যাক আবারও হেসে বলল, টু কোল্ড; নো ম্যাডাম প্রবলেম!
আমি আর অ্যালাস্টার হাসলাম।
তারপর জ্যাক ও অ্যালাস্টার চলে গেল শুতে। যাওয়ার সময়ে জ্যাক হাত নেড়ে বলল, মি? ওয়ান ওয়াইফ। ইচ পোর্ট।
আমি আর অ্যালাস্টার আবার হাসলাম।
ওরা চলে যেতেই দেখি সারা নেমে আসছে সিঁড়ি বেয়ে।
ও বোধহয় জেনি আর ক্যারলের মতোই বাড়তি জামা-কাপড় আনেনি। এসে অবধি সেইদিনের ফ্লেয়ার, জিনের শার্ট আর ফুলহাতা সোয়েটার ছাড়া আর কিছু পরতে দেখিনি। একটা চামড়ার জার্কিন শুধু একবার বের করতে দেখেছিলাম কেম্পটেনের রাতে।
বললাম, কী ব্যাপার? তুমি গেলে না নাচতে? সকলেই তো গেল?ও ঠোঁট উলটে বলল, আমার ভালো লাগে না।
কেন? অবাক হয়ে শুধোলাম আমি।
ও বলল, এমনিই।
তারপর আমাকে আর কিছু বলতে না দিয়ে বলল, হাঁটতে যাবে? আমার ঘরের জানলা দিয়ে দেখলাম বাইরে ফুটফুটে জ্যোৎস্না-আল্পসের চুড়োগুলো রুপোলি পাত দিয়ে মোড়া বলে মনে হচ্ছে।
আমি বললাম, চলো। দরজা খুলে বেরোতেই বুঝলাম কীরকম ঠাণ্ডা বাইরে। সারাকে বললাম, তোমার শীত করবে না?
ও বলল, এখনও করছে না, করলে দেখা যাবে।
তারপরই দুষ্টুমি করে মুখ ঘুরিয়ে বলল, সঙ্গে সমর্থ পুরুষমানুষ থাকলেও যদি কোনো মহিলার শীত করে তাহলে কিছুই বলার নেই।
আমি হাসলাম। বললাম, ইজরায়েলিরা খুব সাহসী। সব ব্যাপারে।
ও হাঁটতে হাঁটতে ফ্লেয়ারের দু-পকেটে দু-হাত ঢুকিয়ে বলল, আমাদের সম্বন্ধে তুমি কী জানো?
আমি বললাম, বেশি কিছুই জানি না। তবে তোমাদের একচোখে কালো চশমা মোসে দেওয়ানকে দেখে রবিনসন ক্রুসোর আমলের জলদস্যু বলে মনে হয়। শুনেছি, পড়েছি; তোমরা মরুভূমিতে চাষ করো, তোমরা খুব ডেয়ার-ডেভিল জেদি জাত।
ও বলল, জেদি হওয়া কি খারাপ?
আমি বললাম, তা নয়, তবে জেদটা কী কারণে, জেদের প্রার্থিত বস্তু কী তার ওপর সব কিছু নির্ভর করে। ভালো জেদ ভালো; খারাপ জেদ খারাপ।
আমাদের জেদ ভালো না খারাপ?
আমি বললাম, এমন সুন্দর রাতে জেদাজেদির কথা না হয় তুলেই রাখো।
ও হাসল, পকেট থেকে একটুকরো চকোলেট বার করে আমাকে দিল, নিজেও খেল। তারপর বলল, ঠিক বলেছ।
রাস্তায় লোক নেই, জন নেই। দূরের অটোবান দিয়েও এখন কম গাড়ি যাচ্ছে। চাঁদের আলো আল্পসের চুড়োর বরফে পিছলে পড়ে পাহাড়ে বনে ছড়িয়ে পড়েছে। ভারি ভালো লাগছে।
সারা আমার বাঁ-দিকে হাঁটছে। ডান হাত দিয়ে চকোলেট কামড়ে খাচ্ছে কু£রকুটুর করে। ওর সোনালি ডান হাতে একটা প্লাটিনামের বালা-সোয়েটারের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আছে। সেই চাঁদের আলোয় ওর কাটা-কাটা চোখ-মুখ, নীল চোখ, উড়াল সোনালি চুল, আর ঠোঁটের কাছে ধরা রুপো ছোঁয়া সোনালি বালা পরা সোনালি হাত এক আশ্চর্য চলমান স্নিগ্ধ ছবির সৃষ্টি করেছে।
সারা হঠাৎ বলল, সারাটা জীবন এমন ছুটি হলে বেশ হত।
আমি বললাম, তুমি কী করো?
ও বলল, একটা কমপিউটার ফার্মে চাকরি করি এবং লড়াইও করি।
ভাবতেও অবাক লাগল যে, যে-হাতের স্নিধ সৌন্দর্যে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম একমুহূর্ত আগেও সেই হাত দিয়ে ও অটোমেটিক ওয়েপন ছোঁড়ে; মানুষ মারে।
ভাবছিলাম, এমনিতেই সব মেয়েই মানুষ মারে হেলাফেলায়, তাদের আবার শক্ত হাতে বন্দুক ধরার দরকার কী? ভগবান এমনিতেই তো কম মারণাস্ত্রে সজ্জিত করে পাঠাননি তাদের। তবু আরও কেন?
প্রথম দিন থেকেই লক্ষ করেছিলাম যে, এই মেয়েটি বয়েস অনুপাতে অনেক বেশি ম্যাচিওরড। জীবনে ওর যেন সবই জানা হয়ে গেছে। ওর সমবয়েসি অন্য সমস্ত ছুটি কাটাতে-আসা ছেলে-মেয়েরা এতক্ষণ ডিসকোত্থেকে নাচে মত্ত, জুয়ার চাকার পাশে ঘুরছে, বিয়ার খাচ্ছে পাগলের মতো, নিজেদের বেহিসাবি যৌবন নিয়ে যে কী করবে তা ভেবে পাচ্ছে না, ভাবছে যে যৌবনের কোনো তল নেই, ক্ষয় নেই, শেষ নেই; ভাবছে যৌবন অনন্ত।
অথচ এই মেয়েটি যেন যৌবনে পা দিয়েই যৌবনকে লগি দিয়ে মেপে ফেলেছে। জেনে গেছে কত বাঁও জল তাতে। জেনে শুনে সে সাবধানি ভিস্তিওয়ালার মতো শরীর মনের ভিত্তিতে যৌবনকে পুরে নিয়ে মেপে মেপে খরচ করছে। কৃপণরা যেহেতু সবসময়েই সাবধানি হয়, সারার হাঁটাচলা, কথা বলা, চোখ-তাকানো হয়তো সে কারণেই অতিসাবধানি। এটা খারাপও; আর ভালোও। ভাবছিলাম।
সারা হঠাৎ বলল, তোমাদের দেশে একবার যাব ভেবেছি।
আমি খুশি হয়ে বললাম, এসো না। এলে আমার সঙ্গে, আমাদের বাড়িতে, আমার অতিথি হয়ে থেকো। তোমাকে অগ্রিম নেমন্তন্ন জানিয়ে রাখলাম। আমাদের দেশ ভারি সুন্দর। তোমাকে আমাদের গ্রাম দেখাব, জঙ্গল পাহাড় দেখাব, দেখবে আমাদের দেশের লোকেরা কত ভালো।
যাব, একবার। অস্পষ্ট স্বরে বলল সারা।
হঠাৎ সারা বলল, আমার একা একা হাঁটতে খুব ভালো লাগে।
আমি বললাম, আমরা সকলেই তো একা; সারাজীবন একা। তবু শুধু একা একা হাঁটতেই ভালো লাগে কেন তোমার? একা একা বাঁচতে ভালো লাগে না?
ও বলল, না। আমরা যে সকলেই একা, চিরজীবনের মতো একা একথা জানি বলেই একা একা বাঁচতে ভালো লাগে না।
তবে একা একা হাঁটতে ভালো লাগে কেন?
ভালো লাগে, কারণ একা একা হাঁটবার সময়ে অনেক কিছু ভাবা যায়। নিজেকে একা পেলে নিজের শুভাশুভ, ভবিষ্যৎ, ভালোমন্দ এসব ভাবনা নিয়ে নাড়াচাড়া করা যায়। নিজেকে জানা যায়। তোমাদের গীতায় নিজেকে জানা সম্বন্ধে কীসব কথা আছে না?
আশ্চর্য। আমি বললাম।
তারপর শুধোলাম, তুমি গীতা পড়েছ?
পুরো পড়িনি। ইংরিজিতে গীতার ওপরে একটা বই পড়েছিলাম। তোমাদের কর্মযোগ। তোমরা কিন্তু দারুণ জাত। তোমাদের মতো ঐতিহ্য খুব কম জাতের আছে।
আমি বললাম, একজন আঠারো-উনিশের বিদেশি মেয়ের পক্ষে এত ঔৎসুক্য আমাদের দেশ সম্বন্ধে, ভাবলেও ভালো লাগে।
সারা বলল, আমার মা ও বাবা দুজনকে আমার তেরো বছর বয়েসে একইসঙ্গে, একই দিনে হারিয়েছিলাম। তারপর থেকে জীবন, জীবনের মানে এসব সম্বন্ধে অনেক কৌতূহল জাগে আমার। যা আমার বয়েসি মেয়ের পক্ষে স্বাভাবিক নয়, এমন অনেক বিষয়ে আমি পড়াশুনা করেছি। করি।
তারপরই বলল, অন্যায় করেছি?
আমি হাসলাম। বললাম, অন্যায় কীসের? তোমার সঙ্গে আলাপ হয়ে আমার গর্বিত লাগছে নিজেকে।
হঠাৎ সারা বলল, তুমি একা এসেছ কেন দেশ বেড়াতে?
আমি কী জবাব দিই ভেবে পেলাম না।
আশ্চর্য। ও বলল।
কেন? আশ্চর্য কেন?
আমি শুধোলাম।
তোমার এমন একা একা নির্বান্ধব হয়ে ঘুরে বেড়াতে কষ্ট হয় না? মনের কথা না হয় বাদই দিলাম। শরীরের কষ্টও বোধ করো না তুমি?
আমি বললাম, শরীরের কষ্টটা তত সহজেই লাঘব করা যায়। আসল কষ্ট তো মনের। সেটাই আসল কষ্ট।
হঠাৎ সারা বলল, জানি না। আমার তো মনে হয় শরীরটাও মনের মতো। ইকুয়ালি ইম্পরট্যান্ট! তোমরা ভারতীয়রা শরীরটাকে নেগেটিভ করে একটা বাহাদুরি পাওয়ার চেষ্টা করো। আমার কিন্তু মনে হয় এটা ঠিক নয়। জীবনে শরীরটা মনের মতোই ইম্পরট্যান্ট। শরীরকে পুরোপুরি অস্বীকার করে কি তার দাবিকে দাবিয়ে রেখে কি মানুষ সুস্থভাবে বাঁচতে পারে?
আমি বললাম, সুস্থতা বলতে তুমি কী মনে করো জানি না। তবে বাঁচতে যে পারে, এ বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই।
ও আমার দিকে তাকাল একবার। তারপর বলল, তুমি কি সত্যিই নিঃসন্দেহ এ সম্বন্ধে, না শেখানো কথা বলছ; অথবা সংস্কারের কথা।
তারপর হঠাৎ অত্যন্ত বিজ্ঞর মতো বলল, সংস্কারকে কাটিয়ে ওঠাও কি মনুষ্যত্ব নয়? সংস্কার এবং যাবতীয় সংস্কারই কি ভালো?
আমি বললাম, আমার কোনোরকম সংস্কার নেই। সংস্কারবদ্ধতা একরকমের পরাধীনতা। সংস্কারে আমার বিশ্বাস নেই।
সারা বলল, তুমি সত্যি কথা বলছ না।
আমি অবাক হয়ে বললাম, একথা কেন বলছ?
বলছি, কারণ তোমায় পরীক্ষা করলে তুমি পরীক্ষায় পাস করবে না।
আমি হাসলাম। বললাম, করো পরীক্ষা। কী পরীক্ষা করতে চাও তুমি?
সারা বলল, আজকে তুমি আমার সঙ্গে শোবে। আমার খুব একা লাগছে; শীতার্ত লাগছে। পারবে তুমি আমার শীত কাটাতে, আমার একাকীত্ব ঘোচাতে? যে একাকীত্ব একজন মাতৃ পিতৃহীন উনিশ বছরের সঙ্গীহীন লড়াই করা মেয়ের মেরুদন্ডে, মজ্জায় সেঁধিয়ে আছে–যে শীত সমস্ত সত্তায় ছেয়ে আছে সেই শীতকে তুমি উষ্ণ করে তুলতে পারবে? যদি পারো, তাহলে জানব যে, তুমি যথার্থ পুরুষ। যথার্থ সংস্কারমুক্ত জীব।
আমি অবাক হয়ে সারার মুখে তাকালাম। চাঁদের আলোয় ওর সোনালি কাটাকাটা মুখকে খুব নিষ্ঠুর অথচ করুণ দেখাচ্ছিল।
বললাম, ঠিক আছে। তবে হোটেলে ফিরে চলল।
সারা আমার হাতটা ওর হাতে টেনে নিল।
বলল, এখুনি নয়। বাইরের শীতটা আরও একটু লাগুক। ঠাণ্ডায় আমার ঠোঁট ফ্যাকাশে হয়ে যাক। আমার সমস্ত শরীর হিম হয়ে উঠুক। তখন, তখন তুমি ধীরে ধীরে আমাকে উষ্ণতায় ভরে দিয়ে।
আমি বললাম, জানো আমার একটা উপন্যাস আছে, তার নাম একটু উষ্ণতার জন্যে। ফর আ লিটল ওয়ার্মথ। সেই উপন্যাসের উপজীব্য বিষয় হল যে, আমরা সকলেই এই শীতার্ত নির্বান্ধব পৃথিবীতে একটু উষ্ণতার জন্যে, একটু উষ্ণতার কাঙালপনা নিয়ে বেঁচে থাকি। উষ্ণতাই জীবন, উষ্ণতার অভাবই মৃত্যু। জীবনের অভাব।
সারা বলল, স্ট্রেঞ্জ। ঠিক আমার মতটাও এই। কিন্তু তুমি কোন ভাষায় লেখো?
আমি বললাম, বাংলায়। আমার মাতৃভাষায়।
ও বলল, তোমার ইংরিজিতে লেখা উচিত। আমাদের পড়তে দেওয়া উচিত তোমার বই। বাংলায় লিখলে তো আমরা পড়তে পারব না। নয়তো অনুবাদ করাও।
যখন আমরা ফিরে আসছিলাম, তখন রাত সাড়ে দশটা। আল্পসের মাথায় লক্ষ্মীপূর্ণিমার চাঁদ অঝোরে ঝরছে। ঠাণ্ডায় কান জমে যাচ্ছে। আমি আমার ওভারকোটটা খুলে সারার গায়ে পরিয়ে দিলাম।
ও বলল, তোমার শরীরের উষ্ণতা তোমার ওভারকোটে সব মাখামাখি হয়ে আছে। তুমি বুঝি তোমার সম্পূর্ণ ভুমির বদলে শুধু তোমার ওভারকোটটা দিয়েই ছুটি চাও? বলেই দুষ্টুমি করে হাসল ও একটু।
আমি শুধোলাম, হাসছ কেন?
ও বলল, হাসছি এই ভেবে যে, চিরদিনই কি আমার সব শীত তুমি এমনি করে ঢেকে রাখতে পারবে? দু-দিনের আলাপ। দু-দিন পরে এই ট্যুর শেষ হয়ে গেলেই সব শেষ হয়ে যাবে। তবে এই ধৃষ্টতা কেন?
আমি বললাম, কারণ, ভবিষ্যতে আমার বিশ্বাস নেই। ব্যক্তিগত ভবিষ্যৎ, জাতির ভাগ্য ও সমষ্টির ভবিষ্যৎ এসবই বোধ হয় বানানো কথা। একমাত্র বর্তমানটাই সত্যি। বর্তমানের মুহূর্তগুলোর সমষ্টি নিয়েই জীবন। কখনো ভুলেও এর ভাবনা ভেবে বর্তমানকে মাটি কোরো না। অন্তত আমি কখনো করতে চাইনি। এই মুহূর্তের সত্যকে নিয়েই দারুণভাবে বেঁচে থাকো; উপভোগ করে প্রতিটি মুহূর্ত। জীবন মানেই তো মুহূর্তের গাঁথা মালা। তাই মুহূর্তটাও কি ফেলে দেবার!
হোটেলে ফিরে সারা আমাকে তার নিজের ঘরে নিয়ে গেল। আমাকে চেয়ারে বসিয়ে রেখে আমার সামনে নিরাবরণ হল। তার সোনালি মরুভূমির মতো পেলব জ্বালাধরা যুবতী শরীরের উষ্ণতা আমার প্রবাসের সমস্ত শীতকে মুছে দিল!
সারা বলল, এসো, ভবিষ্যৎ-এর মুখে ছাই দিয়ে আজকের এই মুহূর্তটিকে আমরা উষ্ণতায় ভরিয়ে তুলি।
ঘরের আলো নিবিয়ে দিয়েছিল ও। জানালার কাঁচ বেয়ে চাঁদের আলো এসে ঘরের কার্পেটে, বিছানায় পড়েছিল। জানালা দিয়ে আল্পসের তুষারাবৃত চুড়োগুলো দেখা যাচ্ছিল। নীচে অন্ধকার উপত্যকা।
সারা ফিসফিস করে বলল, কই এসো!
আমার বুকে শুয়ে সারা ফিসফিস করে বলল, আমাকে দারুণ দারুণ আদর করো তুমি, খাজুরাহোর দেশের লোক, কোনারকের দেশের লোক, আদরে আদরে তুমি আমার শৈশবের কৈশোরের প্রথমযৌবনের সমস্ত কষ্ট, গ্লানি, একাকীত্ব সব নিঃশেষে মুছিয়ে দাও। আমাকে সম্পূর্ণতার আনন্দে আপ্লুত করো। আমার সব অতীত ভবিষ্যৎ ভুলিয়ে দাও।
জবাবে কোনো কথা না বলে আমি ওর চোখের পাতায় চুমু খেলাম।