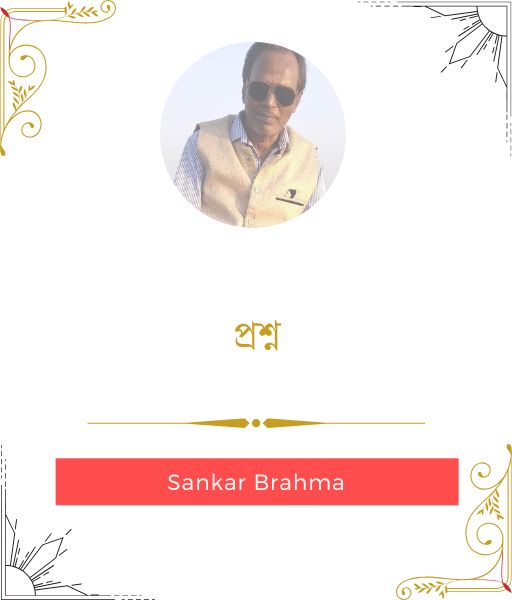পোলিশ কবি চেসোয়াভ মিউশ, তাঁর কবিতা ও সাক্ষাৎকার -1
’’জীবন সংগ্রামে মানুষের আত্মরক্ষার জন্য দু’টি সৃজনশীল হাতিয়ার হচ্ছে জ্ঞান আর কল্পনা। প্রাকৃতিক অবস্থা এবং মানব সমাজের বিভিন্ন পর্যায়কে বীক্ষণ ও পর্যালোচনা করার দক্ষতা, যার সাহায্যে সম্ভব হচ্ছে জ্ঞান বা চিন্তনের বিকাশ। কল্পনা যদিও একধরণের চিন্তন মানব মনের সচেতন প্রক্রিয়া, কিন্তু এ ক্ষেত্রে চিন্তার প্রকাশ ইমেজে। বলা যেতে পারে কল্পনা এমন এক শক্তি যার সাহায্যে মানুষ প্রাকৃতিক বিষয়বস্তুতে মানবিক গুণ.অনুভূতি ও বৈশিষ্ট আরোপ করে থাকে।’’
সঙ্গত কারণেই সৌন্দর্য সৃষ্টির নিয়মানুযায়ী শিল্প-সাহিত্য-কবিতায় যুগ ও সমাজ পরিবর্তনের ছাপ তাৎক্ষণিক নয়।
’মানুষের সামাজিক সত্তাই তার চৈতন্যের নির্ধারক’।
স্বাভাবিক ভাবে শিল্প-সাহিত্যিকরা যা কিছু নির্মাণ করেন তার মধ্য দিয়ে সামাজিক অবস্থানের চেতনাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মিউসের কবিতায় আমরা এই সত্য মোটামুটি ভাবে লক্ষ্য করা যায়।
চেসোয়াভ মিউশ-আমেরিকায় নির্বাসিত পোলিশ-কবি, সাহিত্যে নোবেল পেয়েছে ১৯৮০ সালে। তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতার অনুবাদ করেছেন মানবেন্দ্র বন্দোপাধ্যায়। বিশ্ব সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত এতো বড় একজন কবি(চেসোয়াভ মিউশ)-এর কবিতা প্রসঙ্গে বলবার আগে কবির সৃষ্টিকে বার বার পড়ে, বুঝে, (সময় নেয়া, পড়া, এবং পঠিত বিষয়গুলোর অনুভূতিকে অন্তরঙ্গ করে শিল্পসত্তার ভেতরে প্রবেশের চেষ্টা করা।) তাঁর সৃষ্টির কালকে অনুধাবন করে তবেই তাঁকে বোঝা যাবে।
কবির স্বদেশ পোল্যান্ড বেশ কয়েকবার বাইরের আক্রমণের মুখে পড়ে এবং তার স্বধীনতা বিপর্যস্ত হয়। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধকালে ১৯৩৯ সালে জার্মানরা আকস্মিক আক্রমণ করে পোল্যান্ড দখল করে নেয়। পোলিশ সেনাবাহিনীর সামান্য প্রতিরোধ কোনো কাজে আসেনি। ফ্যাসিষ্টরা দখল করার পর দখলে এগিয়ে আসে সোভিয়েত বাহিনী এবং তারা পোল্যান্ডের শ্বেত রুশিদের অধ্যুষিত এলাকা প্রায় ৭৫ হাজার বর্গ কিলোমিটার-এর ভাগ জার্মানদের কাছ থেকে গ্রহণ করে নিজদের নিয়ন্ত্রণে নেয় । শুরু হয় প্রতিরোধ যুদ্ধ। এই যুদ্ধে কমিউনিষ্টরা প্রাধান্য বিস্তার করে এবং লাল ফৌজের সহযোগিতায় পোল্যান্ড মুক্ত হয়। এ’সব ঘটনাবলী কবির আবেগ আর অনুভূতিকে নানা ভাবে আলোড়িত করেছে এবং তার সৃষ্টিতে মৌলিক অনুসঙ্গ হয়ে আছে ।
কবি পরবর্তীকালে পোল সরকারের বর্হিদেশের কুটনৈতিক দপ্তরে সংষ্কৃতি বিভাগের প্রধান হয়ে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং ’কোল্ড ওয়্যার’ যুগে আমেরিকাতে আশ্রয় নিয়ে প্রবাসী হয়েছেন । আর এভাবেই তিনি দেশান্তরী কবি হিসেবে পরিচিতি পেয়েছেন । কেন তিনি তা’ করেছেন তার কোনো উল্লেখ কবি পরিচিতিতে নেই। অনুমান তো করাই যায়, যদিও কবি প্রবাসী তবু তিনি ঐ সমাজের সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে বসবাস করে নিজভূমির ইতিহাস ঐতিহ্যকে আশ্রয়-প্রশ্রয়-অবলম্বন করে তার সৃষ্টিকে সক্রিয় রেখেছেন ।
কবি তাঁর ’উৎসর্গপত্র’ কবিতায় বলেছেন ’কাকে বলে কবিতা, যদি তা না-বাঁচায় /দেশ কিংবা মানুষ?’
কবিতা মানুষকে বাঁচাবে কিংবা বাঁচার দাবীতে সোচ্চার হবে, মানুষ কে আশান্বিত করবে এবং হতাশা ও গ্লানি থেকে মুক্তির জন্য মানুষকে উদ্দীপ্ত করবে এমনটা যদি না হয় তো তাকে কবিতা বলবো কেন? কিন্তু তবুও কতো রকমের কবিতা রোজ লিখিত হচ্ছে পৃথিবী জূড়ে, আর তাতে কতো মত পথ ইত্যাদিরও প্রয়োগ রয়েছে। কিন্তু এমন উচ্চারণ তো সবটাতে আর থাকছে না যে ’যদি তা না বাঁচায় দেশ-মানুষ’ । এই ধরণের পঙক্তি নিশ্চয়ই ভিন্ন করে রূপ দিচ্ছে কবিতার উচ্চারণে।
মিউশের এই কথার সঙ্গে সঙ্গেই থিয়োডর আডোরনোর সেই বিখ্যাত কথাটিও আমাদের মনে পড়বে : To write lyric poetry after Auschwitz is barbaric, ( আউশউইটজের পরে গীতিকবিতা লেখা বর্বরতা) বা তাদেউশ রুজেভিচের কথা, They forget/ that contemporary poetry/ means struggle for breath।(তারা ভুলে যায়/ সমসাময়িক কবিতা/ মানে নিঃশ্বাসের সংগ্রাম।) এইভাবেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কবিতার মনস্তত্ত্ব ও অনুভব বদলে যেতে শুরু করে কিছু কবিকে আশ্রয় করে। এখানে মনে রাখা উচিত, যুদ্ধোত্তর নন্দন ও আলোকদীপ্তির ভাবনায় তাৎপর্যগত পরিবর্তন এসে গেল, কবিতা প্রথাগত নন্দনবোধ আর শিল্পভাবনায় নিজেকে আটকে রাখল না, ধরতে চাইল ননদনতত্ত্বের ও আলোকায়নের দ্বন্দ্বগুলোকে, তাদের খোলনলচে গেল পালটে। আডোরনো এবং হোর্কহাইমার তাঁদের বিখ্যাত কাজ ডায়ালেকটিক অব এনলাইটেনমেন্টে বলেছেন, তথ্যপ্রবাহ এবং ব্র্যান্ড-নিউ বিনোদন মানুষকে অধিকতর স্মার্ট করেছে ঠিকই; কিন্তু তার চেয়েও বেশি করেছে নির্বোধ। সৌন্দর্যের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে যা ক্যামেরা উৎপাদন করে। সংস্কৃতি এখন আপাতবিরোধী পণ্য আর বিজ্ঞাপন হলো জীবনের সর্বরোগহরকর বিশেষ একটা-কিছু। তাঁরা তাঁদের বিখ্যাত গ্রন্থে আরো বলেছেন, অষ্টাদশ শতকের আশাবাদ বা মানবতাবাদ এক চূড়ান্ত ভ্রান্ত ধারণা, কান্টের ‘আলোকদীপ্তি কী’ এক বাতিল বিষয় ছাড়া আর কিছু নয়। যুদ্ধ দেখিয়ে দিয়েছে যে, পশ্চিমা সভ্যতার অন্তরালে অপেক্ষায় রয়েছে এক পশুশক্তি , যে সুযোগ পেলেই ঘাড় মটকে ধরতে ভুল করে না। এই প্রতি-ভাবনা ও রূপান্তরের পরিপ্রেক্ষিতে বিংশ শতাব্দীর কবিতা ভাবনার যে-সমস্ত ভাঙচুর এবং পরিবর্তন এলো , তার অন্যতম পুরোহিত হলেন চেসোয়াভ মিউশ।
’এইতো পোল্যান্ডের সব অগভীর নদী-ধোঁয়া উপত্যকা।
আর এক বিশাল সেতু
শাদা কুয়াশায় চ’লে যাচ্ছে।
এই যে ভাঙাচোরা শহর,
আর হাওয়া ছিটিয়ে দেয় তোমার কবরের ওপর গাং-চিলের চীৎকার,
যখন আমি তোমার সঙ্গে কথা বলি’।
গাংচিল নদী-নির্ভর পাখি, নদীর মাছ খেয়ে সে বাঁচে, তার কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ-তীব্র, সচকিত করে চার-পাশ এবং কখনও কখনও ইঙ্গিতবাহী হয়ে ওঠে ’আর ভাঙাচোরা শহর’ উপমা হিসেবে জীবন ও জীবিকার বিপর্যস্ততাকে তুলে আনছে সেই তুমির ক্ষেত্রে যাকে কবি বাঁচাতে পারেননি। শুধু তা’ কবি নয় আরো অনেককে, অনেক সহযোদ্ধা যাঁরা বাঁচেনি কিংবা যারা বেঁচে গেছেন, আকুতিটা নিজের মধ্য থেকে বৃহত্তের দিকে সম্প্রসারিত… ‘এবং আমি তোমার সঙ্গে কথা বলি নিশ্চেতনা থেকে’ … এই ধরণের উচ্চারণ আমাদেরকে অন্যরকম ব্যঞ্জনাময় অনুস্বরের মধ্যে প্রবেশের সুযোগ করে দেয়। পাশাপাশি এরকম সরল ব্যাঞ্জনাধর্মী পঙক্তির বিস্তার আমরা লক্ষ্য করতে পারি। ’কোন নাগরিকের গান’ কবিতায় ’আমি দেখেছি দেশগুলোর পতন আর কত জাতির নরকবাস, রাজা ও সম্রাটদের পলায়ন, স্বৈরাচারীদের ক্ষমতা।’ ’কোন নাগরিকের গান’ কিংবা ’কাফে’ কবিতাটির – ’কাফের সেই টেবিলটায় যারা বসতো
যেখানে শীতের দুপুুরে জানলার কাঁচে ঝলসে উঠতো বাগানের তুহিন
শুধু অমিই বেঁচে আছি একা’
একদম সাদা-মাটা বিবৃতি কিন্তু ব্যঞ্জনাময়, দুপুর আছে, শীতও আছে কাফের সেই টেবিলটা ও আছে, কিন্তু আরও যারা ছিলো একদিন এবং একদিন যারা এমন শীতের দুপুরে এখানে থাকবে বসবে বলে আশা করা গেছে তারা আর নেই। এমন ’নেই হয়ে যাওয়ার’ স্মৃতিগুলো যা চেতনে অবচেতনে জাগ্রত দিনের মতো
’অবিশ্বাস ভরে আমি ছুঁই তুহিন মর্মর
অবিশ্বাস ভরে আমি ছুঁই আমার নিজের হাত’– এক দ্বান্দ্বিক সংকোচন ও সম্প্রসারণ পাঠককে মুগ্ধতা দেয় ।
১৯৪৪ সালে লেখা এই কবিতাটি পাঠককে স্মরণ করিয়ে দেবে পোল্যান্ডের মানুষের প্রতিরোধ যুদ্ধ, যুদ্ধের ভয়াবহতা আর সেই যুদ্ধে হারিয়ে যাওয়া তাজা প্রাণগুলোকে,
’কারণ আমি-তো এখনও জানি না মানুষের হাতে ম’রে যওয়াটা সত্যি কী, ওরা জানে ওরা জানে তার সব’।
এই কবিতাটা আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে হারিয়ে যাওয়া মানুষদেরকেও যেন একই ভাবে স্মরণ করিয়ে দেয়, একই ভাবে বলা যায় সবই আছে ওরা নেই, অথচ ওরাই জানে মানুষের হাতে মরে যাওয়ার সত্যিটা, ওরা জানে তার সব, শুধু এদিকের এরা আজও জানে না, তাই এতো বিপত্তি ।
আধুনিক কালের মনীষীরা সারা পৃথিবীকে তাঁদের সৃজন ক্ষমতা দ্বারা প্রভাবিত করেছেন, তাঁদের সর্বাগ্রগণ্যদেও মধ্যে আছেন মার্কস, ডারউইন আর ফ্রয়েড । বলা যেতে পারে তাঁদের জ্ঞানালোক দ্বারা তারা মানব জীবন বুঝতে জানতে এবং তা ভালোভাবে উপলব্ধি করতে বিপুল অবদান রেখে গেছেন, যা আজো সারা পৃথিবীকে ভাবিয়ে চলছে, আলোড়িত করছে। ্ডারউইনের আবিষ্কার যুগ-যুগ ধরে প্রগতিরুদ্ধ মানুষদের জানতে চিনতে বুঝতে শিখিয়েছে জীবন বিকাশের নিয়মাবলী, আর মার্কসের সমাজত্ত্ব, দর্শন সমাজ রাষ্ট্র, রাজনীতি অর্থনীতি যে গতি দিয়েছে তা’ শুধু মাত্র রাষ্ট্র-রাষ্ট্রক্ষমতার মধ্যেই সীমিত থাকেনি, বরং জীবনকে আমূল বদলাতে প্রয়োজনীয় বহু বিষয়ে মানুষকে বিপুল প্রেরণা দিয়ে যাচ্ছে । শিল্প-সহিত্য সহ নানা সৃজনশীল কাজে তার প্রভাব পড়েছে অপরিসীম । ফ্রয়েডের মনস্তত্ত্ব ’ ঈশ্বর অপরিবর্তনীয়, ধ্রুব বিশ্বাসের প্রতীক’ – মানুষের এই সনাতন মূল্যবোধে প্রচন্ড আঘাত হানলো। তার আবিষ্কৃত মনস্তত্ত্ব বলছে, মানুষের চেতনা সংহত কোন পদার্থ নয়, চেতনার আলো দূরবিস্তৃত এক অতল অন্ধকারে, যা নিয়ন্ত্রিত হয় চেতনার ক্রিয়া-কলাপে । ফ্রয়েড তত্ত্ব প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানেই যখন ভারতবর্ষে পৌঁছালো তখন তা’ এখানকার শিল্পী-সাহিত্যিকদের মানসিক জগতেও আলোড়ন তুলেছিলো। রবীন্দ্রনাথের সাথে ফ্রয়েডের সাক্ষাত হয়েছিলো ১৯২৬ সালে ২৫ অক্টোবর, ভিয়েনায়। ফ্রয়েড-এর তত্ত্ব সম্পর্কে তিনি অবহিত ছিলেন, জীবনের শেষের দিকে আনন্দরূপের জয়গান করতে করতে মনের আদিমতম রূপকেও তিনি অস্বীকার করতে পারেননি,
‘অচেতন তোমার অঙ্গুলি
অস্পষ্ট শিল্পের মায়া বুনিয়া চলিছে
আদি মহার্ণব গর্ভ হতে
অকস্মাৎ ফুলে ফুলে উঠিতেছে
প্রকাশে স্বপ্নের পিঞ্জর
বিকালাঙ্গ,অসম্পূর্ণ ’
’তুমি মোরে দিয়েছ কামনা.
অন্ধকার অমারাত্রি সম’
বা
‘শত শত শুকরের চিৎকার সেখানে
শত শত শুকরীর প্রসব বেদনার আড়ম্বর’’
এমনি অনেক পঙক্তি রচিত হয়েছে বাংলা কবিতায়। ফ্রয়েডের মনস্তত্ত্ব খুব বেশী বিস্তার পেয়েছে জীবনানন্দ দাশের কবিতায়, এ জন্যে কোন কোন সমালোচক তা’কে নিশ্চেতনার কবি বলেও অভিহিত করেছেন । যদিও আমার মনে হয় কখনও কোন কবিকে বিশেষ কোন অভিধায় অভিহিত করা যুক্তি-যুক্ত নয়। কবি যে কবি, এটাই তার সার্থক পরিচয় । ফ্রয়েড ’চেতন ও অবচেতনের’ নিচে আর একটি স্তরের কল্পনা করেছেন যাকে বলা হয়েছে প্রাগ-চেতনা; এতে থাকে সেই সব অভিজ্ঞতা যা এক সময় মানুষ উপভোগ করেছে। প্রাগ চেতনার মধ্যস্থলে দাঁড়িয়ে থাকে মনের প্রহরী, ফ্রয়েড যাকে বলেছেন ‘সুপার ইগো’। মনের অনেক কামনা বাসনা যা সমাজ কাঠামোয় প্রকাশ অসংগত ’সুপার ইগো’ তা’ প্রকাশে অনুমতি দেয় না । তার এ তত্ত্বের বিপরীত মতও আছে এবং বিধান নিয়েও নানা সময়ের আলোচনা আছে। ইয়ঙ এবং পাভলভ প্রমূখরা ভিন্ন কিছু মতামত এবং বিধানের কথাও বলেছেন। সে প্রসংগ এখানে আলোচ্যে বিষয় নয়, তবে কাব্যে শিল্পে ফ্রয়েডের এই আবিষ্কার শিল্প শৈলী, চিত্রকল্প বিষয়বস্তু ইত্যাদিতে প্রয়োগ পেয়ে সৃষ্টিকে যে আরো গভীর, ব্যঞ্জনাময় করে তুলেছে এবং গতানুগতিকতাকে ভেঙে শিল্পী-কবি-লেখক সৃজনশীল মানুষকে এবং তার পাঠককে নতুনতর নির্মাণ শৈলীর ভুবনে প্রবেশ করতে দিয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। মিউশের অনেক কবিতায় মনস্তাত্ত্বিক প্রয়োগ সার্থকভাবে আছে ।
‘কোন দেশকে ভালোবেসো না :
দেশগুলো চট ক’রে উধাও হ’য়ে যায়
কোন শহরকে ভালোবেসো না ;
শহরগুলো সব চট করে আবর্জনার স্তূপ হ’য়ে পড়ে..
অতীতের সব দিঘিগুলোর দিকে তাকিয়ো না…এমন এক মুখ যা তুমি কখনও প্রত্যাশা করোনি’।
মিউশের কবিতাগুলোর ভিতরে লক্ষ্য করলে আমরা চেতন-অবচেতন আর অচেতন-এর নানা উপস্থিতি উপলব্ধি করতে পারি । নির্বাসিত জীবনে তিনি আমেরিকায় আর জন্মসূত্রে তিনি পোলিশ, পোল্যান্ডের ভূমি, বাতাস, মানুষ প্রান্তর তার চেতনা জুড়ে থাকলেও বর্তমান সময়, অবস্থা-অবস্থান-পারিপার্শিকতায় তার অনেক ইচ্ছে, কর্ম, সাধনা নানা রূপ বিরূপতায় ধূসর হয়ে উঠেছে। ওই সব দিনগুলোর স্মৃতি হারিয়েও যায়নি , আবার প্রকাশ পারঙ্গমও নয়, তাই তারা নানা প্রতীকী ব্যাঞ্জনায় উঠে আসছে এই ভাবে
’পশু শক্তির জয়ী হবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না আমরা বাস করি সফল ন্যায় বিচারের যুগে’; ‘আবার পশুশক্তির কথা উচ্চারণ কোর না, নয়তো তুমি সোপর্দ হবে
গোপনে-গোপনে হেরে যাওয়া সব মতবাদ মেনে নাও
যার শক্তি আছে ,তারই আছে ঐতিহাসিক যুক্তিপ্রক্রিয়া..’
এভাবে দ্বৈত বাক-বিন্যাসের মধ্য দিয়ে তিনি একটা সিদ্ধান্ত দিতেও চেয়েছেন এক আত্মগত প্রশ্ন আর জবাবে।
অনুবাদকের মিউশ প্রসংগে তার জীবন ভাষ্যে দেখা যায় যে প্রতিরোধ যুদ্ধের সময় পোল্যান্ডের আন্ডারগ্রাউন্ড পার্টির সক্রিয় সদস্য, মার্কসবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। স্বভাবতই তার কবিতায় তাঁর অঙ্গীকার মানবতার পক্ষেই থেকেছে, তিনি ভুলে যাননি তার পোল্যান্ডকে আবার বন্ধন ছিঁড়েও ফেলেননি তার প্রবাসী জীবনের সামাজিক রাজনৈতিক পরিবেশ । অবশ্য যারা পার্টি সহিত্য বলতে রাজনৈতিক শ্লোগান বোঝেন. তাদের কথা আলাদা। অথচ মার্কস শিল্পীদের সম্পর্কে যথেষ্ট অনুরাগ প্রকাশ করেছেন। তিনিও তাঁর কন্যারা শেকসপীয়র ভক্ত ছিলেন। ‘জোসেফ ভাইদেমেয়ারের’ কাছে লিখেছিলেন কবি তিনি যেমন মানুষই হোন না কেন, কিছু প্রশ্রয় ও প্রশংসার দাবী রাখে। .. হাইনেকে ভালোবেসে ফরাসী সরকারের কাছ থেকে অর্থ নেয়ার কলঙ্ক থেকে তাকে রক্ষার চেষ্টাও করেছেন। ফলে এখানেই উপলব্ধির পার্থক্য। জে. অপ্রেসিয়ান ’স্বাধীনতা এবং শিল্পী’ বই-এ সিদ্ধান্ত আকারে জানিয়েছেন যে ’মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দৃষ্টিতে শিল্পীর স্বাধীনতার অর্থ হচ্ছে জনগণের স্বার্থে জনগণের বৌদ্ধিক জীবনের সমৃদ্ধির জন্যে জনগণের সঙ্গে অগ্রসর হওয়া’।
তবুও শিল্প-সহিত্য প্রসংগে আলোচনার বিপরীতে আলোচনার শেষ নেই, বোধ করি শেষ হওয়াও উচিৎ নয়। কবি সহিত্যিকরা কোনো পার্টির সদস্য কিনা তা’ জরুরী নয়, যা প্রয়োজন তা হলো তিনি তার কাজে সৎ এবং সাহসী ছিলেন কিনা এবং সঠিকভাবে জীবনকে উপলব্ধি করে তার সৃষ্টিতে প্রতিফলন ঘটিয়েছিলেন কিনা, আর পাঠক তার রসাস্বাদনের মধ্য দিয়ে সুন্দরের অনুভবে একটি সত্যে পৌঁছাতে পারলেন কিনা। যেমন করে বলেছেন রবীন্দ্রনাথ, ’সত্যই সুন্দও, সুন্দরই সত্য’। এটা কীটসেরও বক্তব্য। আর সে সত্য হচ্ছে মানুষ, মানুষের বেঁচে থাকার সংগ্রাম আর সুন্দর হলো তার চেতনা। তাই সত্য উচ্চারণের মধ্য দিয়ে কবিকে পৌঁছাতে হয় বিস্তৃত চেতনায় । তার জন্য একজন কবির যেমন দরকার আবেগ তেমনি দরকার কল্পনা এবং বলবার মতো নিজস্ব ভাষা। তার আরো জানতে হয় নির্মাণ কৌশল আর উপযুক্ত সম্পাদনা। মিউশের কবিতায় এর সম মাত্রা ও পুষ্টির উপস্থিতি আছে।
(#)
বিশাল জীবন (১৯১১-২০০৪), অনেক কবিতা, অন্য লেখালেখি আর খ্যাতি, প্রতিষ্ঠা, পুরস্কার নিয়ে মিউশ কী করলেন? কীভাবে দাঁড় করালেন তিনি নিজেকে? কিংবা কী সেই ভাঙচুর যা তাঁকে চিহ্নিত করে স্বতন্ত্র হিসেবে? এই নিরিখে আমরা বলতে পারি, তা ছিল আসলে বের হয়ে আসার আকাঙ্ক্ষা। তাঁর মন ও ইচ্ছাকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়া। কবিতার যে প্রথাগত ধারণা এবং ফর্ম, এর ভেতর থেকে নিজেকে পৃথক করা। মিউশ বলেছেন, বিংশ শতাব্দীর ভয়ংকরতার মধ্যে তাঁর জন্ম, আধুনিক ইতিহাসের দুই বিশাল সর্বগ্রাসী অবস্থা, জাতীয় সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের মধ্যে তিনি বসবাস করেছেন। দেখেছিলেন ছিলেন দুই-দুটি বিশ্বযুদ্ধ। তা ছিল এক আত্মবাস্তবতা, সে-কারণে ফরাসি প্রতীকবাদী অনুসারীদের মতো তিনি বিশুদ্ধ কবিতার রাজ্যে পালাতে পারেননি। তিনি লিখেছেন অতীতকে নিয়ে, ট্র্যাজিক ও শ্লেষাত্মকভাবে। ‘আর্স পোয়েটিকা?’ কবিতায় তিনি বলেছেন, ‘…that I’ve devised just one more means/ of praising Art with the help of irony।’ ( যে আমি বিদ্রুপের সাহায্যে শিল্পের প্রশংসা করার আরও একটি উপায় আবিষ্কার করেছি।’) সাবজেক্টিভ আর্ট এবং অবজেক্টিভ আর্টের মধ্যে তিনি তাই শেষোক্তটির সমর্থক ছিলেন, এবং তিনি দাবিও করেছেন যে, তাঁর কাব্যের অনুশীলনই এর প্রমাণ দেবে। এসব কিছুও আপতিক নয়, আমাদের মাথায় রাখতে হবে, থিয়োডর আডোরনো, তাদেউশ রুজেভিচ বা জবিগনিয়েভ হেরবের্টসহ আরো অনেককে কবিতাকে অন্যভাবে দেখেছেন। তাই তিনি বলতে পারেন অনায়াসে : ‘শপথ করে বলছি, আমার কাছে কোনো শব্দের চাতুরী নেই/ মেঘ বা বৃক্ষ যে-ভাষায় কথা বলে, আমি তোমার সাথে সেই নৈঃশব্দ্যের ভাষায় কথা বলি।’ অর্থাৎ তিনি অনুসরক ছিলেন না আগেকার ধারার, বরং সময়ের ভাষা ও কবিতাকে লিখতে চেয়েছেন তিনি। শুদ্ধ কবিতার লালিতপালিত রূপ এবং সৌন্দর্যসৃষ্টি থেকে সরে এসে ভিন্ন-এক প্রায়াসে নিজেকে সৃষ্টিশীল রেখে ছিলেন তিনি, যা মানুষের অন্য-এক সংলগ্নতার কথা বলে। তিনি মনে করতেন, দৃশ্যমান বাস্তবতা কবিতার স্বাস্থ্যকে উন্নত করে। এজন্যই তিনি বলেছেন, কবিতা তাঁর কাছে সাম্প্রতিক মানবিক দোলায়িত সময়ের এক অংশগ্রহণ। তবে এ-কথাও তিনি বলেছেন যে, তিনি কবির নিষ্ক্রিয়তা বা প্রতিক্রিয়াহীনতাতে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন, যা কবিকে উপহার দেয় এক-একটি কবিতা যা বস্ত্তত উঠে আসে তাঁর গভীর চিন্তা বা ধ্যান থেকে। এসবই তাঁর কবিতায় স্থায়িত্ব নিয়েছে সফলভাবে। তাঁর কবিতার ভাষা ও স্বরসংগতি তাঁর নিজেরই মতো, যা অন্তর্গতের কণ্ঠকে চিনিয়ে দেয়। তিনি বলতেও চান আত্মকথন বা স্বীকারৌক্তিক ধরণে ও উচ্চারণে এবং এই প্রবণতা তাঁর সমগ্র জীবনের শর্তেই যেন প্রকাশিত।
মিউশ, যদিও পোল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করেননি, তবু তিনি নিজেকে পোলিশ কবি বলেই মনে করতেন, কারণ তিনি নেটিভ মাতৃভাষা পোল ভাষাতেই লিখতেন। পরবর্তী সময়ে তিনি বলেওছেন যে, ভাষাই তাঁর স্বদেশ। পোল্যান্ডে তিনি জন্মগ্রহণ করেননি, থাকেনওনি বহু বছর। তিনি জন্মগ্রহণ করেন লিথুয়ানিয়ায়, ১৯১১ সালে, তাঁর কৃষক পিতামহের ছোটো তালুকে। মিউশ এই গরীব লিথুয়ানিয়াকে আখ্যায়িত করেছেন ‘কবিতা এবং পুরাণের দেশ’ বলে। ‘নেটিভ রেল্ম’ গ্রন্থে তিনি আরো বলেছেন, যখন ভূমধ্যসাগরীয় এলাকায় রাজ্যের পতন আর উত্থান হচ্ছিল আকছার, সে-সময়ে লিথুয়ানিয়া ছিল কুমারী অরণ্যে ছাওয়া এক অঞ্চল যেখানে উপকূলে মাঝেমধ্যে ভাইকিংদের জাহাজ ভেড়া ছাড়া আর কিছুই ঘটত না। তিনি বলেছেন, ‘মানচিত্রের জ্ঞানসীমানার বাইরে এটা ছিল বাস্তব অপেক্ষা অধিক পৌরাণিক।’
মিউশের শৈশব হয়েছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণে টালমাটাল। তাঁর পিতা, আলেকজান্ডার ছিলেন সড়ক প্রকৌশলী এবং যুদ্ধের সময় তাঁকে জারের বাহিনীতে কাজ করতে হয়েছিল। এ-সময় রাশিয়ার যুদ্ধ-এলাকায় সেতু নির্মাণের কাজে তাঁকে নিয়োজিত থাকতে হয়েছিল, আর মিউশ ও তাঁর মাও তাঁর সঙ্গে একসঙ্গে ছিলেন। এই স্মৃতির কথা বলতে গিয়ে মিউশ বলেছেন, ‘আমাদের ঘর ছিল প্রায় সময়ই এক ঢাকা ওয়াগন।’ ১৯১৮ সালে তাঁদের পরিবার লিথুয়ানিয়ায় ফিরে আসে। এখানে তাঁর শৈশব ছিল প্রশান্তময় আর এখানেই অতঃপর রাজধানী ভিলনিয়াসে তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু হয়। তিনি আট বছর উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন এবং তা ছিল অনেকটা ক্যাথেলিক গোছের শিক্ষা। এ-বিষয়ে তিনি বলেন, প্রতিদিনই শুরু হতো প্রার্থনা দিয়ে আর সেখানে গীত হতো সেই গান : ‘যখন ভোরের আলোরা জেগে ওঠে।’ ক্যাথেলিক মতবাদ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, ক্যাথেলিক বিশ্বাস বা মতবাদ খুবই শক্ত মতবাদ, কারণ তা যেন সত্যিই ধরে রেখেছে কতিপয় ভূতাত্ত্বিক স্তরপরম্পরা। ১৯৩৩ সালে ২১ বছর বয়সে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ আ পোয়েম অন ফ্রোজেন টাইম এবং দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ থ্রি উইন্টার ১৯৩৬ সালে প্রকাশিত হয়। তিরিশের দশকে তিনি নিজেকে যুক্ত রাখেন ক্যাটাসট্রোফিস্ট স্কুলের কবিদের সঙ্গে। ক্যাটাসট্রোফিজমের মানে হলো, চূড়ান্ত মূল্যবোধের সমূলে ধ্বংসসাধন, বিশেষত সেই মূল্যবোধ যা একটি এগিয়ে দেওয়া সাংস্কৃতিক পদ্ধতির জন্য প্রয়োজনীয়। তবে তা কিছু নির্দিষ্ট মূল্যবোধকে, কিছু ঐতিহাসিক রূপায়ণকে দূর করতে চায় বলে দাবি করেছিল, মোটেই মানবতাকে নয়। মিউশ এখানেই আইনশাস্ত্রে ডিগ্রি লাভ করেন এবং এরপর পারিতে বৃত্তি নিয়ে এক বছর কাটান। সাহিত্য নিয়ে না পড়ে আইন নিয়ে পড়ার কারণ হিসেবে তিনি বলেন, যদি তিনি কী হতে চান তা আগেই প্রকাশিত হয়ে যেত তাহলে নিজের কাছেই পরাজিত হয়ে যেতেন যেন। তবে বৃত্তিটা ছিল আইন নয়, বরং সাহিত্যের ওপর রাষ্ট্রীয় বৃত্তি। সেখানে তিনি তাঁর দূরবর্তী সম্পর্কের ভাই অস্কার মিউশের দেখা পান, যিনি ছিলেন ফরাসি কবি, এবং মিউশ তাঁর দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হন সে-সময়। সে-সময়ের তাঁর নিজ চিন্তা-বিষয়ে তিনি বলেছিলেন, ‘সকল তরুণ কবির মতো আমিও বিশ্বাস করতাম যে, সমসাময়িক শিল্পে কিছু গোপন জায়গা আছে, আর আছে এক সুতো যা একজনকে গোলকধাঁধার ভেতরে নিয়ে যায়।’ অস্কার মিউশ তাঁর একটি কবিতা বিখ্যাত এক রিভিয়্যু পত্রিকায় প্রকাশ করেন। পরবর্তীকালে মিউশ স্বীকারও করেছেন, তাঁর ওপর অস্কার মিউশের প্রভাব ছিল তুমুল, বিশেষত শৈলীর দিক থেকে। প্যারিস রিভিয়্যুকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এ-প্রভাবের বিষয়ে তিনি জানিয়েছিলেন : ‘বস্ত্তত আইনস্টাইনেরও আগে, তিনি স্বতঃলব্ধভাবে, আপেক্ষিকতার এক মহাবিশ্বতত্ত্বকে অনুধাবন করতেন – এক মুহূর্ত যখন সেখানে কোনো স্থান নেই, পদার্থ নেই, কাল নেই; এই তিনটিই, তাঁর কল্পনাশক্তিতে, এক গতিময়তার সাথে সম্পর্কিত ছিল।’
ভিলনিয়াসে সোভিয়েত শাসনের সময় মিউশ তাঁর যৌবনের শহর থেকে পালিয়ে নাৎসি-অধিকৃত ওয়ারশতে চলে যান। সেখানে তিনি সমাজতান্ত্রিক প্রতিরোধে অংশগ্রহণ করেন। সে-সময়ে তাঁর নাৎসিবিরোধী কবিতা সংকলন অজেয় কবিতা আন্ডারগ্রাউন্ড প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়, যেখানে তিনি লেখেন ‘জগৎ’ এবং ‘ভয়েসেস অব পুয়োর পিপল’। ১৯৩৯ সালে যুদ্ধ শুরু হলে পোল্যান্ড নাৎসি জার্মানির ও রাশিয়ার অধিকারে চলে যায়, মিউশ প্রতিরোধ আন্দোলনে নিজেকে যুক্ত করেন। এ-সময়ে কবিতাবলি নামে এক সংকলন জে. সিরাক ছদ্মনামে প্রকাশ করেন তিনি। ওয়ারশর পতনের পর তিনি ক্রাকাওয়ের বাইরে কিছুদিনের জন্য অবস্থান করেন। ১৯৪৫ সালে স্টেট পাবলিশিং হাউস তাঁর কবিতা সংকলন রেসকিয়্যু প্রকাশ করে। ওয়ারশতে প্রতিরোধ কার্যক্রমের সময়টাতে নিজের কবিতাতে তাঁর প্রভাব সম্পর্কে তিনি বলেন, কবি হিসেবে তখন তিনি ছিলেন অস্বাভাবিক, কারণ তাঁর মনে হয়েছিল, কবিতা আগের মতো আর পৃথিবীকে মেলে ধরতে পারে না, আর এর জন্য দরকার ভিন্ন পথের। অর্থাৎ কবিতা লিখলেও তাকে হতে হবে অন্যরকম। এখানে অবস্থানকালীন টি.এস. এলিয়টের কবিতারও অনুবাদ করেন তিনি। দ্য ওয়েস্ট ল্যান্ডকে তাঁর মনে হয়েছিল বিপর্যয়কর এবং গভীরভাবে ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপাত্মক।
যুদ্ধের পর মিউশের জীবনে অন্য পরিবর্তন আসে। মিউশ পোলিশ কমিউনিস্ট সরকারের কালচারাল অ্যাটাশে হিসেবে নিউইয়র্ক ও ওয়াশিংটনে কাজ করেছিলেন এক বছরের মতো। যখন তাঁকে পোল্যান্ডে ফিরে আসার জন্য বলা হয়, তখন তিনি তা করতে অস্বীকৃতি জানান। ১৯৫১ সালে তিনি পোলিশ সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে ফ্রান্সে রাজনৈতিক আশ্রয় নেন। এই ফিরে না-যাওয়া বিষয়ে তিনি বলেন, তিনি জানতেন তাঁর দেশ এক সাম্রাজ্যের প্রদেশ হয়ে যাচ্ছিল। তিনি আরো বলেন, নতুন সাম্যবাদী বিশ্বাসকে তিনি অস্বীকার করেছেন কারণ মিথ্যাই ছিল তার প্রধান অনুজ্ঞা, আর সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা বস্ত্তত ছিল মিথ্যারই আরেক নাম। কমিউনিস্ট শাসনে তাঁর মুখোমুখিতা ও অভিজ্ঞতা তিনি তুলে ধরেন তাঁর দ্য ক্যাপটিভ মাইন্ড বইয়ে। পাশ্চাত্যে এটিকে সর্বগ্রাসী মানসিকতার এক মৌলিক ও অসাধারণ গ্রন্থ হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। সে-সময়ে পারি থেকে তাঁর কবিতা সংকলনও প্রকাশিত হয়। পারিতে তিনি অনুবাদক ও ফ্রিল্যান্স লেখক হিসেবে কাজ করেন। দশ বছরের ফ্রান্স-অবস্থান খুব সুখকর হয়নি বিশেষত সমাজতন্ত্রী ও কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের বিচারে। এই সময়ে তাঁর দুটি উপন্যাস – সিজার অব পাওয়ার, দ্য ইসা ভ্যালি আর বিখ্যাত গদ্যগ্রন্থ দ্য ক্যাপটিভ মাইন্ড প্রকাশিত হয়। দ্য সিজার অব পাওয়ার হলো তাঁর আত্মজৈবনিক উপন্যাস। ক্ষমতা যখন বদলায় তখন কীভাবে বাঁচতে হয়, এটিই এই উপন্যাসের ভাব। প্রকৃতপক্ষে দ্য সিজার অব পাওয়ার আর দ্য ক্যাপটিভ মাইন্ডের মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে। দুটোতেই বর্ণনাতীত যন্ত্রণা এবং পোল্যান্ডের দুর্ভাগ্যের অবস্থাকে দেখানো হয়েছে। এই বইয়ে মিউশ আহবান করেছেন পশ্চিমকে পূর্ব ইয়োরোপকে ঠিকভাবে অনুধাবন করার জন্য। দ্য ক্যাপটিভ মাইন্ডে তিনি দেখিয়েছেন, সর্বগ্রাসী শাসন কালে শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীদের নৈতিক স্খলন। এ-গ্রন্থে তিনি লিখেছেন, যখনই তিনি জীবনের সৌন্দর্যে বুঁদ হয়ে থাকেন, ঠিক তখনই একটি ইমেজ তাঁর কাছে ফিরে ফিরে আসে : ‘চোখের সামনে দেখলাম, সর্বদা একই তরুণী ইহুদি বালিকা। সম্ভবত সে ছিল বিশ বছর বয়সী। তার শরীর ছিল পূর্ণ, চমকপ্রদ, উল্লাসময়। সে রাস্তায় দৌড়াচ্ছিল, তার হাত ওপরে তোলা, বুক সামনের দিকে। সে তীব্রভাবে চিৎকার করে উঠল, ‘না! না! না!’ মৃত্যুর অনিবার্যতা তার বোধের বাইরে – যে-অনিবার্যতা বাইরে থেকে এসেছে, যা তার অপ্রস্ত্তত শরীরের সাথে স্বাভাবিক নয়। চিৎকারের মধ্যেই এসএস গার্ডের স্বয়ংক্রিয় পিস্তলের গুলি তাকে বিদ্ধ করল।’ ১৯৪১-৪৩, এই সময়ে ওয়ারশ গেটোতে প্রায় চার লাখ ইহুদি ধ্বংস হয়। দ্য ক্যাপটিভ মাইন্ডে মিউশ লিখেছেন যে, ওয়ারশ গেটোর ট্র্যাজেডি নিয়ে, যার একজন চাক্ষুস সাক্ষী ছিলেন তিনি, তাঁর পক্ষে লেখা ছিল এক কঠিন কাজ। ইহুদি নিধনযজ্ঞের এক বছর পর পোলরা ১৯৪৪ সালে ওয়ারশ অভ্যুত্থানের মাধ্যমে শহরকে মুক্ত করার এক সাহসী কিন্তু সর্বনেশে উদ্যোগ গ্রহণ করে। শহরের উপকণ্ঠে মিউশ ধরা পড়েন। হিটলারের বাহিনী তাঁকে এক অস্থায়ী ট্রানজিট ক্যাম্পে আটক রাখে। সে-রাতেই এক সাহসী ও কর্তৃত্বপরায়ণ নানের মাধ্যমে তিনি উদ্ধার পান, যে-জার্মান কর্তৃপক্ষের ওপর জোর খাটিয়েছিলেন যে, তিনি মিউশের আন্টি হন। তিনি তাঁর নাম জানতে পারেননি। ৬৩ দিনে আঠারো হাজার সৈন্য ও দুই লাখ বেসামরিক মানুষ মারা যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে সুন্দর বারোক শহরের পঁচাশি ভাগই ধ্বংস হয়ে গেল। যুদ্ধের সময় এবং যুদ্ধ-পরবর্তী অনেক কবিতাতেই তিনি গভীর সমবেদনায় যুদ্ধে নিহতদের কথা বলেছেন। যেমন ১৯৪৫ সালে লিখিত ‘উৎসর্গ’ কবিতায় তিনি যা লিখেছেন :
তুমি – যে-তোমাকে আমি বাঁচাতে পারিনি
আমার কথা শোনো।
এই সরল কথাটা বোঝার চেষ্টা করো তুমি,
যেহেতু অন্য কোনোরকম কথাই আমাকে লজ্জা দেবে।
আমি শপথ করে বলছি, আমার মধ্যে কথা দিয়ে কোনো
হাতসাফাই
কোনো চালাকি নেই।
আমি তোমাকে বলছি স্তব্ধতার ভাষায়, যে-ভাষায় কথা বলে
কোনো মেঘ কিংবা গাছ।
যা আমাকে শক্তিমান ক’রে তুলেছিলো, কারণ তুমি ছিলে
মারাত্মক।
একটা যুগের বিদায় আর নতুন যুগের সূচনাকে তুমি মিশিয়ে
ফেলেছিলে,
তুমি মিশিয়ে ফেলেছিলে ঘৃণার অনুপ্রেরণার সঙ্গে গীতল সৌন্দর্য,
অন্ধ পশুশক্তির সঙ্গে সুসম্পাদিত আকার।…
কাকে বলে কবিতা, যদি তা না-বাঁচায়
দেশ কিংবা মানুষকে?…
ওরা কবরগুলোর ওপর ছড়িয়ে দিতো খুদকুড়ো কিংবা আফিম ফুল
পাখির বেশ ধ’রে যারা ফিরে আসবে সেইসব মৃতদের খাওয়াতে।
এখানেই আমার এই বই রাখি আমি, তোমার জন্য, যে-তুমি
একদিন বেঁচে ছিলে
যাতে তুমি আর আমাদের হানা না-দাও।
(অনুবাদ : মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)