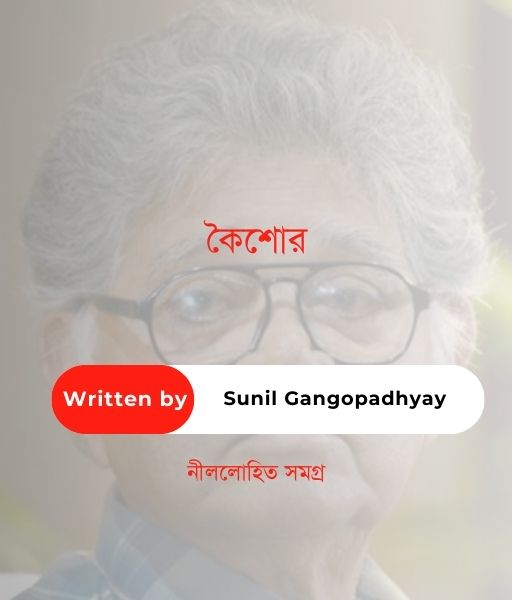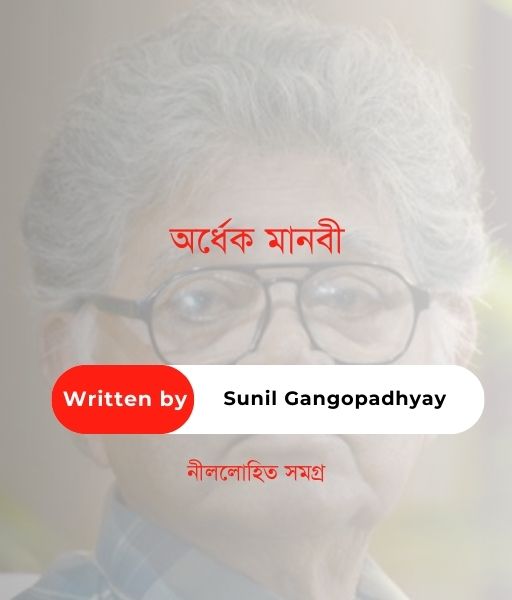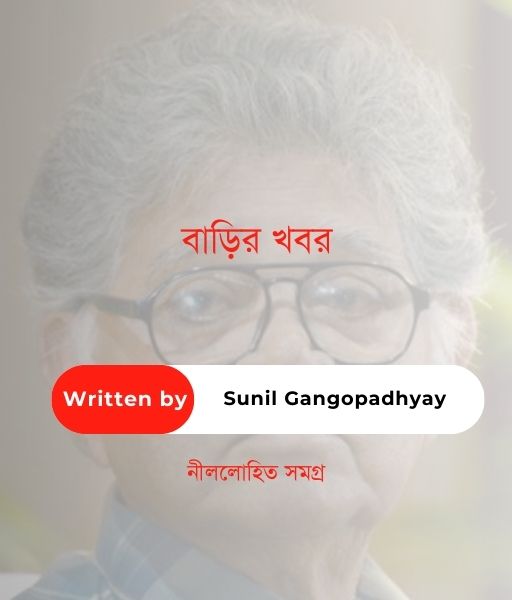নীললোহিতের চোখের সামনে – সংযোজন “খ”
১
এক নববিবাহিত দম্পতির কথা দিয়েই শুরু করি। দুজনের সংসার, দক্ষিণ কলকাতায় ছোট্ট ফ্ল্যাট। স্বামীটি রোজ সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরে আসে, মার্চ মাসে অফিসের কাজ বেশি পড়ায় ফিরতে-ফিরতে আট-নটা হয়। একদিন রাত এগারোটা বেজে গেল। তারপর সাড়ে-এগারোটা, পৌনে-বারোটা। উদ্বেগে, দুশ্চিন্তায় তরুণী বধূটির পাগল হয়ে যাবার মতন অবস্থা। আত্মীয়স্বজন বিশেষ কেউ নেই, নিজেদের টেলিফোন নেই, পাশের ফ্ল্যাটের ফোনও খারাপ। বেপরোয়া হয়ে মেয়েটি বেরিয়ে প’ড়ে অত রাতে একটি ট্যাক্সি ধরল, তার স্বামীর ঘনিষ্ঠ সহকর্মীর বাড়িতে খোঁজ নিতে যাবার জন্য। স্বামীটিকে হঠাৎ এয়ারপোর্টে যেতে হয়েছিল, সে তখনই অফিসের গাড়িতে ব্যাকুল মুখে ফিরছে। নির্জন রাস্তায় বিপরীতমুখী ট্যাক্সিতে এক তরুণীকে দেখে সে দারুণভাবে চমকে উঠল। প্ৰথমে ভাবল চোখের ভুল, তারপর চেঁচিয়ে বলল, থামো, থামো! দুটি গাড়ি থামবার পর স্বামী-স্ত্রীতে মিলন। স্ত্রীটি যখন কাঁদছে, তখন ট্যাক্সিটির ড্রাইভার নেমে এসে বলল, দেখুন দাদা, ইনি আমার গাড়ি ধরতে এসে বললেন, শুনুন, আমি আমার স্বামীকে খুঁজতে যাচ্ছি, আমার সঙ্গে কোনও খারাপ ব্যবহার করবেননা! আচ্ছা বলুন দাদা, আমরা কি সবাই খারাপ লোক! এই দেখুন-না, দিদি ট্যাক্সিতে হ্যাণ্ডব্যাগ ফেলেই নেমে এসেছেন। আমি যদি দেখতে না-পেতুম…। স্বামীটির দুই চক্ষু বিস্ফারিত। দিনেরবেলা যে ট্যাক্সি ড্রাইভাররা ডাকলে সাড়া দেয়না, হাওড়া যেতে যাদবপুর যাবার প্রস্তাব দেয়, যাদের মুখের ভাব দেখলে গা জ্ব’লে যায়, রাত্তিরে সেই ট্যাক্সিওয়ালার কাছ থেকে এ কী অভাবনীয় ব্যবহার! তার সুন্দরী, যুবতী স্ত্রীকে দিদি ব’লে সম্বোধন করছে!
এটা কিন্তু কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। কলকাতায় মেয়েরা সন্ধের পর একা স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করতে পারে, একা ট্যাক্সি ব্যবহার করতে পারে। নারী-লাঞ্ছনার ঘটনা এ-শহরে খুবই বিরল, ঘটেনা বললেই চলে। নির্জন অন্ধকারে ছিনতাইকারীরা কোন মহিলার গলার হার ধ’রে টান মারতে পারে ঠিকই, কিন্তু স্বর্ণালঙ্কারের বদলে গোটা শরীরটাই অপহরণ করার রীতি এখানে নেই।
জীবন্ত শহর, ফ্লাই-ওভারে পরিপূর্ণ দিল্লিতে কিন্তু সন্ধের পর মেয়েদের এ—স্বাধীনতা অকল্পনীয়। কয়েক বছর আগে এক সরকারি বাসের ড্রাইভার-কণ্ডাক্টর মিলে এক যাত্রিণীকে স্বস্থানে নামতে না-দিয়ে ডিপোতে নিয়ে গিয়ে শ্লীলতাহানি করেছিল। বাস স্টপে অপেক্ষমানা মেয়েদের চলন্ত সাইকেল-আরোহীরা চুল ধ’রে টান মারে। কয়েকদিন আগে খুসবন্ত সিং লিখেছেন যে শক্ত সমর্থ জোয়ান পুরুষরাও ইদানীং সন্ধের পর দিল্লির রাস্তায় বেরুতে ভয় পায়। শিখ-দাঙ্গা ও দূতাবাসকর্মী খুনের পর অতি তৎপর পুলিশ যখন-তখন, যে-কোন লোককে ধরে তল্লাশী ও জেরা করে। একটু রাত হলেই রাজধানীর অধিকাংশ রাজপথ একেবারে শুনশান। কোনও প্রাণের স্পন্দন পাওয়া যায়না।
মাস দু-এক আগে বেলজিয়ামের এক কবি তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের ফরাসী স্ত্রী—কে নিয়ে এসেছিলেন কলকাতায়। নববধূকে নিয়ে মধুচন্দ্রিমা যাপনে। শুনে তো আমি থ। চতুর্দিকে আমি কলকাতার নিন্দে শুনতে পাই, সাহেবসুবোরা তো কলকাতার নামে নাক সিঁটকোয়। কেন্দ্রীয় পর্যটন দফতর বিদেশী ভ্রমণকারীদের আকর্ষণ করবার জন্য যে-প্রচার চালায়, তাতে কলকাতার নাম ভুলেও উচ্চারণ করেনা। তাহ’লে এই সাহেব-মেম মধুর রসে আকৃষ্ট হয়ে কলকাতায় চ’লে এল কী ক’রে?
কবির নাম ভেরনের লাম্বার্সী, তার নবোঢ়ার নাম প্যাট্রিসিয়া। কবিটি তাঁর দেশের শীর্ষস্থানীয়, ঘুরেছেন বহু দেশ, বাস করেছেন অনেক নগরীতে, এই নিয়ে কলকাতায় তাঁর তৃতীয়বার আগমন। কেন এই ফিরে ফিরে আসা? ভেরনের বললেন, মানুষ দেখতে। এই শহরে এত মানুষ, পথে-পথে গিসগিস করছে মানুষ, অট্টালিকায় মানুষ, বস্তিতে মানুষ, নদীর ধারে মানুষ, খেলার মাঠে মানুষ। এত মানুষ, তবু তাদের চোখে হিংস্রতা নেই। মুখের দিকে স্বচ্ছভাবে তাকায়। কারুর দিকে হেসে তাকালে হাসি দিয়ে তার জবাব আসে। মানুষের চেয়ে আর বেশি দর্শনীয় কী আছে? কলকাতাকে আমার সবসময় খুব জীবন্ত লাগে। নেভার এ ডাল মোমেন্ট, ইউ সি!
প্যাট্রিাসিয়া তার পাগলাটে স্বামীর কথা শুনেই শুধু আসেনি। কলকাতা সম্পর্কে আগে সে পড়াশোনা ক’রে নিয়েছে। আন্তর্জাতিক গাইড বইগুলিতে কলকাতা বিষয়ে যে-সব ভীতিকর কথাগুলি আছে, তা-ও তার জানা। তবু কলকাতা সম্পর্কে তার কৌতূহল ছিল। সে খোলা মন নিয়ে এসেছে, তার কিছু—কিছু খারাপ লাগছে, কিছু-কিছু ভালো লাগছে। সে কৌতূহলীভাবে জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা, কী ব্যাপার বলো তো। দিল্লিতে ব’সে আমরা যখন কলকাতার সফরসূচি তৈরি করছিলুম, তখন পর্যটন দফতরের এক কর্তা ভুরু কুঁচকে বললেন, কলকাতায় যাবেন কেন? কী দেখবার আছে? কলকাতা তো বিচ্ছিরি আর ময়লা, আপনারা বরং মধ্যপ্রদেশে খাজুরাহো দেখতে যান।
আমি একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললুম। তখনও রাজীব গান্ধী কলকাতা সম্পর্কে রাজ্যসভায় অশালীন মন্তব্যটি করেননি। কিন্তু দিল্লির তল্পীবাহক আর হুঁকোবরদারদের মনোভাবও যে এইরকম তা আগে ভাসা-ভাসা শুনেছিলুম, সেদিন সঠিক জানলুম। ঐ-ব্যাটাচ্ছেলেরা বোঝেনা যে বিদেশীদের কাছে ওইসব কথা ব’লে তারা নিজেরাই অপমানিত হয়। অন্য কোন দেশের সরকারি ভারপ্রাপ্ত কর্মীরা দেশের এক অংশের নিন্দে করার কথা কল্পনাও করতে পারেনা। প্যাট্রিসিয়াকে আমি জিজ্ঞেস করলুম, তোমার বর না-হয় কবি, সে অসুন্দরকেও সুন্দর হিসেবে দেখতে পারে। কিন্তু তুমি সত্যি ক’রে বলো তো, কেমন লাগছে আমাদের শহরটা।
প্যাট্রিসিয়া বলল, দ্যাখো, আমরা যখন প্যারিস ছেড়ে দূরের কোন দেশ দেখতে যাই, তখন তো আর ভালো হোটেল, নাইট ক্লাব বা সুন্দর-সুন্দর বাগান দেখতে চাইনা। সে সব তো প্যারিসেই আছে। আমরা দেখতে যাই সেই দেশের নিজস্ব চরিত্র সমেত সব-কিছু। সকলেরই তো ঐতিহাসিক স্তম্ভ, মন্দির বা দূর্গ দেখার দিকে ঝোঁক থাকেনা। আমিও মানুষজন দেখতেই ভালোবাসি। কলকাতায় বেশ বন্ধুত্বপূর্ণ মানুষজন থাকে, তারা সারা পৃথিবীর খবর রাখে, এটাই ভালো লাগছে। ওরে বাবা, বইমেলায় এত ভিড়! গরিব সব মানুষজন, তবু তারা বই কেনে! একটা বস্তির পাশ দিয়ে যেতে-যেতে কী দেখলুম জানো? বাচ্চা ছেলেমেয়েরা খেলাধুলো করতে-করতে খলখল ক’রে হাসছে। এত দারিদ্র্যের মধ্যেও যে মানুষ হাসতে পারে, গান গায় এটা আমরা পশ্চিমী লোকেরা জানতুমইনা!
ভেরনের বললেন, এই শহরে শ-খানেক ছোট পত্রিকা বেরোয়, পাঠের আসরে ভিড় হয়, তুমি জানো? ইণ্ডিয়ার আর কোন শহরে এরকম নেই। আমাদের প্যারিসেও নেই।
প্যাট্রিসিয়া বললে, তবে, শহরের রাস্তাঘাট তোমরা পরিষ্কার রাখলে পার। তাতে তো বেশি পয়সা খরচ হয়না, ওটা মানসিকতার ব্যাপার। যখন-তখন আলো নিভে যায়, এটা কী? এখানকার মানুষ সত্যিই বড়ো সহনশীল। একদিন ওদের বেশ একটা মজার অভিজ্ঞতা হ’ল। যাওয়া হয়েছিল ডায়মণ্ড হারবার পেরিয়ে কাকদ্বীপের কাছাকাছি একটা জায়গায় গঙ্গা-সন্দর্শনে। একটা খোলা নৌকো নিয়ে নদীবক্ষে ভ্রমণ। প্রায় সন্ধে হয়ে এসেছে, আকাশটি বড়ো অপরূপ। কিন্তু সাহেবজাতির সৌন্দর্য উপভোগের ধরনধারনই অন্যরকম। নদী শুধু দেখার জিনিস নয়, অবগাহনের। ভেরনের নদীতে নেমে পড়তে চায়। প্যাট্রিসিয়ার মৃদু আপত্তি, অচেনা জল, কত গভীর বা স্রোত কে জানে, তা ছাড়া হাঙর-কুমীর থাকতে পারে। আমি বললুম না, জলজ জন্তু জানোয়ারের কোন ভয় নেই। সাঁতার জানো তো? ভেরনের তৎক্ষণাৎ শার্ট-প্যান্টালুন খুলে এক ডাইভ মারল। তারপর যখন মুখ তুলল, তার বেশ ভ্যাবাচ্যাকা ভাব। নিচের মাটিতে তার মাথা ঠুকে যাবার উপক্রম হয়েছিল! মাঝ-গঙ্গায় মাত্র কোমর জল, সেখানে সাঁতার কাটবার কোন দরকারই নেই।
প্যাট্রিসিয়া বলল, এ কী, এত বিখ্যাত তোমাদের গঙ্গা নদী, তাতে এত কম জল? এ যে বিশ্বাসই হয়না।
আমি কাঁচুমাচুভাবে বললুম, কী করব বলো! আমাদের এই প্রিয় নদীটিকে নিয়ে আমাদের সরকার কী যে ছিনিমিনি খেলছে! হাজার গণ্ডা বাঁধ দিয়েছে এই নদীর বুকে, তারপর আবার জল ভাগাভাগি, কত কী! নদীগুলির আর স্বাধীনতা নেই!
বন্দরের কাল হ’ল শেষ! পুরোপুরি না-হ’লেও অনেকটা। কলকাতা বন্দরের বেশ-খানিকটা ভার নিয়ে নিয়েছে হলদিয়া, তারপর পারাদ্বীপ। বিমানবন্দরটিও খাঁ-খাঁ করে, এক-একটি বিদেশী বিমানসংস্থা শেষযাত্রায় উড়ে যাচ্ছে। তা যাকনা। তবু এক-একটা বিকেলে যখন জোর হাওয়া দেয়, আকাশের আলোর রকমফের হয়, তখন পথে-পথে অজস্র মানুষের মুখ ঝলমলিয়ে ওঠে। যৌবনের দীপ্তি টের পাওয়া যায়, বেঁচে থাকাটাকেই মনে হয় একটা উৎসবের মতন। আর-একটি বছর পেরিয়ে গেল। কলকাতার আয়ু কি এক বছর কমল না বাড়ল?
২
আমি বাইরের ঘরে ব’সে-ব’সে একটা বই পড়ছিলাম। দুপুরবেলা। চারদিক নিঝুম। আমি তখন বি. এ. পরীক্ষা দিয়ে বাড়িতে ব’সে আছি, রেজাল্ট বেরোয়নি। সিনেমা দেখতে যাবার পয়সাও জোটেনা। প্রচণ্ড রোদ্দুর, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আড্ডা মারারও উৎসাহ পাইনা। দুপুরে ঘুমোনো অভ্যেস নেই আমার—তাই গল্পের বই প’ড়ে সময় কাটাচ্ছিলাম।
দরজায় কড়া ন’ড়ে উঠল। দরজা না-খুলে জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলাম একজন দীর্ঘকায় সন্ন্যাসী দাঁড়িয়ে আছেন। গেরুয়া পরা, মাথায় জটা।
—কী চাই!
সন্ন্যাসী গম্ভীরভাবে বললেন, দরজা খোলো।
কথার টান শুনলে বোঝা যায় বাঙালি নন, তবে বাংলা জানেন। আমি ঠাকুর—দেবতা মানিনা। এমনকি, পরীক্ষা দিতে যাবার সময় কিংবা চাকরীর ইন্টারভিউ দিতে যাবার সময়ও কখনো কালীমন্দিরে প্রণাম করিনি। কিন্তু সন্ন্যাসীদের আমার ভালো লাগে চিরকাল। ঘরছাড়া বিবাগী ভ্রাম্যমাণ মানুষরা আমাকে চিরকাল টানে।
দরজা খুলতেই সন্ন্যাসী গম্ভীরভাবে বললেন, আমার একটা সিকি চাই।
একটু অবাক হয়ে গেলাম। এরকম সুসজ্জিত পুরোপুরি সন্ন্যাসীকে কখনো ভিক্ষে করতে দেখিনি। আশ্রম ইত্যাদির চাঁদা চাইতে কেউ-কেউ আসে বটে, কিন্তু সোজাসুজি ভিক্ষে—
–কেন? আপনাকে সিকি দেবো কেন?
—আমার দরকার। যাও নিয়ে এসো—
—আমার কাছে পয়সা নেই।
সন্ন্যাসী একটুক্ষণ কী যেন চিন্তা করলেন। তারপর বললেন, কিন্তু আমাকে পয়সাটা তো এ-বাড়ি থেকেই নিতে হবে। অন্য কোন বাড়ি থেকে নিলে চলবেনা। আমি হেসে বললাম, কেন, এখান থেকেই নিতে হবে কেন? আমাদের বাড়ির বিশেষত্ব কী?
—এটা ব্রাহ্মণের বাড়ি।
—কী ক’রে জানলেন?
—আমি এসব বুঝতে পারি।
—আপনি দরজার বাইরে নেমপ্লেট দেখেছেন তো? ওটা বাড়িওয়ালাদের। আমরা একতলার ভাড়াটে-ব্রাহ্মণ নই। সন্ন্যাসী আমার চোখের দিকে তীব্রভাবে তাকিয়ে বললেন, ছিঃ! মিথ্যে কথা বলতে নেই।
সন্ন্যাসীর ব্যবহারে বেশ-একটা ব্যক্তিত্ব ছিল। নিছক ভিখিরী মনে হয়না তাঁকে। তবু চার আনা পয়সা চাইছেন কেন? আমি বললাম, আপনি হাত গুণতে জানেন? আমার হাতটা দেখে দিন, তাহ’লে চার আনা পয়সা দিতে পারি। নেহাৎ মজা করার জন্যই কথাটা বলেছিলাম। সন্ন্যাসী আমার ডান হাতটা টেনে নিলেন। ভুরু কুঁচকে বললেন, তুমি তো এবার বি. এ. পরীক্ষা দিয়েছ?
–হ্যাঁ, বলুন তো আমি পাশ করব কিনা!
সন্ন্যাসী কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন আমার হাতের দিকে। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, যাক!
তারপর হাতটা ছেড়ে দিয়ে পেছন ফিরে হাঁটতে শুরু করলেন হঠাৎ। চমকে গিয়ে বললাম, কী হ’ল, চ’লে যাচ্ছেন কেন? দাঁড়ান! দাঁড়ান! নিয়ে যান পয়সা! সন্ন্যাসী কর্ণপাত না ক’রে হনহন ক’রে হেঁটে চ’লে গেলেন।
সেবার সত্যিই আমি বি. এ. পাশ ক’রে গেলাম। ভালো রেজাল্ট হয়নি, কিন্তু মোটামুটি পাশ করতে কোন অসুবিধে হয়নি। আমি তো সন্ন্যাসীর কাছে পাশ করব না ফেল করব—এ-কথাই জিজ্ঞেস করেছিলাম, তাহ’লে পয়সা না-নিয়ে চ’লে গেল কেন?
সেই সন্ন্যাসীর রহস্যের কথা আমি তারপর অনেক ভেবেছি। কোন কুলকিনারা পাইনি। অত ভাবতাম ব’লেই সন্ন্যাসীর মুখটা আমার মনে ছিল।
বছরদশেক বাদে হরিদ্বারে সেই সন্ন্যাসীকে দেখে তাই আমার চিনতে অসুবিধে হয়নি। চেহারা একইরকম আছে, বার্ধক্যের ছাপ পড়েনি। হর-কি-পারি ঘাটে অনেক ভক্ত পরিবৃত হয়ে ব’সে আছেন।
কৌতূহলী হয়ে আমিও ওঁর সামনে বসলাম। একবার একটু সুযোগ পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম, মহারাজ, আপনি কি বছরদশেক আগে কলকাতায় গিয়েছিলেন? সন্ন্যাসী আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, হ্যাঁ। তুমি তখন আমাকে দেখেছিলে? তারপর জিজ্ঞেস করলেন, কী চাই?
আমি হাতটা এগিয়ে দিয়ে বললাম, আমার হাতটা একটু দেখে দেবেন?
—কী জানতে চাও!
—আমি কি কোনদিন কোনো প্রকৃত সন্ন্যাসীর দেখা পাব?
সন্ন্যাসীর মুখখানা বিষণ্ন হয়ে গেল। আমার হাত ছেড়ে দিয়ে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। একটাও কথা না—ব’লে হনহন ক’রে হেঁটে গেলেন গঙ্গার দিকে। জলে পা ডুবিয়ে স্রোত থেকে বাঁচার জন্যে শিকলটা শক্ত ক’রে ধ’রে বললেন, না।
আমার দৃঢ় ধারণা হ’ল, উনি আর একবার ভুল বললেন।
৩
গত তিন বছর ধ’রে যে-মেয়েটি আমাদের বাড়িতে ঘর-মোছা, বাসন-মাজার কাজ করছিল, সে এই মাসে চাকরি ছেড়ে দিল। মেয়েটি সত্যিই খুব কাজের মেয়ে ছিল। আমার স্ত্রীর কাছ থেকে তার নামে কখনও কোন অভিযোগ শুনিনি। মেয়েটির বয়স কুড়ির নিচে। তার নাম সীতা। মেয়েটির সবচেয়ে বড়ো গুণ এই যে, সে কখনও চেঁচিয়ে কথা বলতনা। প্রায় নিঃশব্দে সে প্রতিদিন তার কাজ সেরে যেত।
আমি ওই মেয়েটির নাম ছাড়া তার সম্বন্ধে আর কিছুই জানিনা। ‘কাজের—মেয়ে’দের সঙ্গে বাড়ির পুরুষমানুষদের বেশি কথা বলার নিয়ম নেই। অল্পবয়েসী ঝি-দের সঙ্গে কোনরকম কৌতূহল দেখানো তো পুরুষদের পক্ষে সাঙ্ঘাতিক অপরাধ। সুতরাং তিন বছর ধ’রে একটি মেয়ে আমাদের বাড়িতে যাতায়াত করলেও আমার কাছে সে প্রায় অপরিচিতই র’য়ে গেল।
মাঝে-মাঝেই ঝি-চাকর ছাড়িয়ে দেওয়া এবং নতুন ঝি-চাকর খোঁজা আজকালকার মধ্যবিত্ত সংসারের গৃহকর্ত্রীদের বিলাসিতার অঙ্গ। সকালবেলা আমার স্ত্রী যে তিন-চারটি টেলিফোন করেন কিংবা তিন-চারটি টেলিফোনের ডাক পান, সেইসব কথাবার্তার অনেকখানিই থাকে ঝি-চাকর সংক্রান্ত আলোচনা। ঝি—চাকরদের জন্য কলকাতায় কোন এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ নেই, কিন্তু আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের পরিবারগুলি মিলিয়ে এক-একটা গোষ্ঠির মধ্যে ঝি-চাকর বিনিময়ের চমৎকার ব্যবস্থা আছে। আমার এক বন্ধু একটি ব্রিটিশ মেয়েকে বিয়ে করেছে। সেই মেমসাহেবটিও কিছুদিনের মধ্যেই এমন বাঙালি হয়ে গেছে যে সে-ও সাহিত্য-শিল্প আলোচনার চেয়ে ঝি-চাকর বিষয়ে আলোচনায় বেশি উৎসাহী। দু-মাসের বেশি তার বাড়িতে কোন দাস দাসী ঢেঁকেনা। আমার স্ত্রীকেই তার বাড়িতে নতুন-নতুন দাস-দাসী সাপ্লাই করতে হয়।
সীতা নামের এই মেয়েটি অবশ্য নিজে থেকেই আমাদের বাড়ির কাজ ছেড়ে দিল এবং তার যুক্তিসঙ্গত কারণও আছে! এই মাসে তার বিয়ে হচ্ছে। কাজ ছেড়ে চ’লে যাবার দিন সে হঠাৎ আমাকে প্রণাম ক’রে সলজ্জ গলায় বলল, ‘দাদাবাবু, যাচ্ছি!’ এইসব ক্ষেত্রে কী বলতে হয় তা আমি জানিনা। তাই চুপ ক’রে রইলুম।
এ-পর্যন্ত আমাদের বাড়িতে যত মেয়ে কাজ ক’রে গেছে, তাদের মধ্যে ছ—সাতজনের নাম এবং মুখ আমি মনে রাখতে পারি। আমাদের ছেলেবেলায় ঝিদের কোনো নিজস্ব নাম থাকতনা। তাদের বলা হ’ত, পরেশের মা, পাঁচুর মা ইত্যাদি। এখন অবশ্য ঝিদের সকলেরই নাম থাকে, কয়েকজনের বেশ আধুনিক নাম, এমনকি রবি ঠাকুরের একটি উপন্যাসের নায়িকার নামের একটি ঝি-ও আমাদের বাড়িতে কাজ ক’রে গেছে।
সীতার ঠিক আগেই যে-মেয়েটি আমাদের বাড়িতে কাজ করত, তার নাম ছিল সুবালা। সে তিনদিনের ছুটি নিয়ে দেশে গিয়ে আর ফেরেনি। তখনই রাখা হয় সীতাকে। তার কাজ দেখে আমাদের বাড়ির সকলেই খুশি। কিন্তু তিন মাস পরে একটা গোলমাল লাগল। সুবালা একদিন ফিরে এসে প্রচুর কান্নাকাটি শুরু করল। তার সঙ্গে দুটি বাচ্চা ছেলেমেয়ে। সুবালার কথা শুনে আমি যা বুঝতে পারলুম তা হ’ল এই যে, তার স্বামী আর-একটি বিয়ে করেছে এবং বাচ্চাসমেত তাকে দেশের বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। সে তার পিঠের কাপড় সরিয়ে দেখাল, তার স্বামী তাকে লাঠি দিয়ে মেরেছে, সেই দাগ।
সুবালার কাহিনী শুনে আমার মা যথেষ্ট দুঃখ বোধ করলেও তাকে আমাদের বাড়িতে আবার কাজ দেওয়া সম্ভব হ’লনা। কারণ, সীতাকে তখন ছাড়িয়ে দেবার কোন যুক্তি নেই। তাছাড়া, সুবালার সঙ্গে দুটি শিশু, এদের থাকবার কোন জায়গা নেই, তাদের দায়িত্ব কে নেবে? সুতরাং ওদের কিছু টাকা দিয়ে বিদায় করা হ’ল। আমার স্ত্রী পুরোপুরি শহুরে মেয়ে, গ্রাম সম্পর্কে তাঁর কোন ধারণাই নেই। সেদিন দুপুরবেলা তিনি কাতরভাবে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, সুবালাকে ডির্ভোস না—ক’রেও তার স্বামী আবার বিয়ে করল কী ক’রে? এইরকমভাবে বাচ্চাসমেত বউকে কেউ ইচ্ছে করলেই মেরে তাড়িয়ে দিতে পারে? দেশে কি কোন আইন-কানুন নেই?
আমি হেসে বলেছিলুম, ‘আইনের লম্বা হাত গ্রাম পর্যন্ত পৌছয়না। আইনের বিচার তো শুধু শিক্ষিত আর টাকা-পয়সাওয়ালা লোকদের জন্য। সুবালার মতন মেয়েদের পক্ষে কি কোর্টে গিয়ে মামলা করা সম্ভব?’
‘কিন্তু পুলিশ কিছু করতে পারেনা?’
‘সুবলাকে আগে প্রমাণ করতে হবে যে তার স্বামী সত্যিই দ্বিতীয় বিয়ে করেছে! এটা প্রমাণ করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের নয়। যে নির্যাতিত, তারই। ‘
‘তা ব’লে পুরুষরাও মেয়েদের এখনও ঐভাবে মারবে? এই যুগেও?’
‘আজকাল শুধু শিক্ষিত লোকরাই বৌদের ভয় পায়। শিক্ষার এই একটা কুফল। যারা লেখাপড়া শেখেনা, তারা এখনও মনের আনন্দে বৌকে মারে! যারা বৌকে পেটায় সেইসব পুরুষদের যদি শাস্তি দিতে হয় তাহ’লে সারা দেশের আধখানাই জেলখানা বানিয়ে ফেলতে হবে।’
এরপর আমাকেই সমস্ত পুরুষ জাতির প্রতিনিধি মনে ক’রে আমার স্ত্রী খুব বকাবকি শুরু করলেন।
সুবালার আগে যে কাজ করত আমাদের বাড়ি, তার নাম ছিল নলিনী। তার স্বামী ছিল এবং কলকাতায় একটা বস্তিতেই তারা থাকত। নলিনী কথা বলত খুব বেশি, সেই জন্য সরাসরি তাকে কোন প্রশ্ন না-ক’রেও তার জীবনের কিছু-কিছু ঘটনা আমি শুনতে পেতুম। নলিনীর স্বামী খুবই অসুস্থ, বিছানা ছেড়ে উঠতে পারেনা। সেইজন্য নলিনী আর তার দুই মেয়ে বিভিন্ন বাড়িতে কাজ ক’রে সংসার চালায়। এই কাহিনীতে কোন নতুনত্ব নেই। অনেক ঝিয়ের স্বামীই অসুস্থ বা পঙ্গু ব’লে শোনা যায়। নলিনী নিজেই একবার অসুস্থ হয়ে পড়ায় তার স্বামী এসেছিল আমাদের কাছ থেকে নলিনীর বাকি মাইনে নিয়ে যেতে। লোকটিকে দেখে একটুও অসুস্থ বা পঙ্গু ব’লে মনে হয়নি আমার। বোঝাই যায় লোকটি অলস এবং অকর্মণ্য, সে তার স্ত্রী ও মেয়েদের কাজ করতে পাঠিয়ে নিজে বাড়িতে ব’সে থাকে।
নলিনীর আগে যে ছিল, তার নাম আমার মনে নেই। সে ছিল যথেষ্ট বুড়ি এবং খুব সম্ভবত তাকে বুড়িদি ব’লে ডাকা হ’ত। এই বুড়িদি ছিল বিধবা এবং রীতিমতন চোর। টাকাপয়সা চুরি করতনা অবশ্য! কিন্তু খাবারদাবার দেখলে সে লোভ সামলাতে পারতনা। সংসারে শুধু এক নাতি আছে তার। সেই নাতির জন্যেই খাবারটাবার চুরি ক’রে নিয়ে যেত সে। তার নাতি স্কুলে পড়ে এবং সেই নাতির নানান্ গুণপনার কথা শুনতে হ’ত আমাদের।
দুধের বাটিতে গোপনে চুমুক দেবার অপরাধে সেই বুড়িদির চাকরি যায়। বুড়িদি খুবই তেজস্বিনী ছিল, নিজের অপরাধের জন্য একটুও অনুতপ্ত না-হয়ে সে প্রচুর চেঁচামেচি ও গালাগালি করতে লাগল। যাবার আগে সে সগর্বে ব’লে গেল যে আমাদের বাড়ির চেয়ে অনেক ভালো বাড়িতে, অনেক বেশি মাইনেতে কাজ তার বাঁধা আছে। এরকম কাজ সে আগেই পেতে পারত ইত্যাদি।
এটা প্রায় দশ বছর আগেকার কথা। সেই বুড়িদি আমাদের বাড়িতে ইদানীং প্রায়ই আসে। এখন সে অনেক বেশি বুড়ি হয়ে গেছে। কাজ করার ক্ষমতাও চ’লে গেছে। তার সেই নাতিটি বড় হয়ে চাকরি পেয়েছে এবং বিয়ে করেছে এবং দিদিমাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। সে-বাড়িতে ঢুকতে গেলেই নাতি তাকে লাথি মারে।
বুড়িদি এখন প্রায় ভিখিরি। ঠিক রাস্তায় ব’সে ভিক্ষে করেনা বটে, তবে তার দীর্ঘজীবন ধ’রে যত বাড়িতে কাজ করেছে, সেইসব বাড়িতে মাসে একবার ক’রে যায়। দরজার কাছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ব’সে থাকে। কিছু চাল, ছেঁড়া কাপড় ও দু-একটা টাকা না-দিলে সে নড়েনা।
এইসব দুঃখী স্ত্রীলোকেরা আমাদের বাড়িতে এসে বাসন মাজে ঘর ঝাঁট দেয়, কাপড় কাচে। কিছু টাকার বিনিময়ে আমরা এদের কাজ থেকে স্বাচ্ছন্দ্য ও আরাম কিনি। এদের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে আমাদের কোন মাথাব্যথা নেই।
সীতা নামের মেয়েটি যখন কাজ ছেড়ে যাবার দিন আমায় প্রণাম করল, আমি তাকে মুখে কিছু বলতে না-পারলেও মনে-মনে বললুম, আহা, এ-মেয়েটির যেন ভালো বিয়ে হয়। একে যেন ফিরে আসতে না-হয়।
৪
ষাট-সত্তরটি পরিবার নিয়ে একটি গ্রাম, এইরকম গ্রামের সংখ্যাই তো আমাদের দেশে বেশি। এইরকম গ্রাম এখন শহরের মধ্যেও গজিয়ে উঠছে। শহরের চৌহদ্দি মাপা হয় বিস্তৃতি দিয়ে আর এইসব শহুরে গ্রামের মাপ হয় উচ্চতায়। কোনটা দশতলা, কোনটা বারোতলা। এদের নাম মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিং!
গ্রাম্য গ্রাম আর শহুরে গ্রামের মধ্যে অনেকরকম মিল আছে, প্রধান যা অমিল সেটাই আগে বলি। ঝগড়া থাক বা ভাব থাক, গ্রামের মানুষ সবাই সবাইকে চেনে। শহুরে-গ্রামের মানুষরা একই ছাদের নিচে দিনের পর দিন বাস করলেও অনেকেই অনেকের নামও জানেনা। এইসব লম্বা শহরের ভূতল থেকে ওপরতলা পর্যন্ত একটা বৈদ্যুতিক টানা গাড়ি চলে, সেই গাড়িতে প্রতিবেশীদের মধ্যে দেখা-সাক্ষাৎ হয়। গ্রামের মানুষ অনেকসময় গরুর গাড়ি বা সাইকেল থামিয়ে অন্যদের সঙ্গে হেঁকে গল্পগুজব করে। আর শহুরে-গ্রামের টানা-গাড়িতে যাতায়াত করার সময় যাত্রীদের নিঃশব্দে, নিজের জুতোর দিকে তাকিয়ে থাকাই নিয়ম। দৈবাৎ কারুর সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেলে একটা ভুরু নাচাতে কিংবা ঠোঁট সামান্য ফাঁক ক’রে হাসির ভান করতে হয়।
জল যেমন জলকে চায়, মানুষও সেইরকম মানুষের সঙ্গে মিশতে চায়। কিন্তু শহরের কায়দাই হচ্ছে কেউ কারুকে চিনিনা এই ভাব ক’রে থাকা, মনে-মনে ইচ্ছে থাকলেও গায়ে প’ড়ে ভাব করার উপায় নেই। তারপর যখন শহরের মধ্যে এইরকম সব লম্বা-লম্বা গ্রাম তৈরি হ’ল অমনি গ্রাম্য স্বভাবটাও ফিরিয়ে আনার একটা সুযোগ পাওয়া গেল। গ্রামের মানুষ একসঙ্গে মেলে কোন উৎসব উপলক্ষে। অতএব শহরের এইসব গ্রামেও লাগাও পুজো! কলকাতার মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিংগুলির একতলার আঙিনায় এখন দুর্গাপুজোর চল শুরু হয়েছে খুব।
এই পুজোতে ধর্মের জন্য ব্যাকুলতা নেই, কেননা এখানকার বাসিন্দারা আধা—সাহেব। এইসব বাড়িতে শ্রীযুক্ত ও শ্রীমতীরা থাকেননা, থাকেন মিস্টার ও মিসেসরা। যদিও চাঁদা ক’রে পুজো, চাঁদার জোরজুলুম নেই, সব ফ্ল্যাটের একই নির্দিষ্ট চাঁদা। ধরা যাক্, ফ্ল্যাট-প্রতি পঞ্চাশ টাকা। মনে করুন, এইরকম একখানা বাড়িতে রয়েছে সত্তরটি পরিবার, তাহ’লে মোট চাঁদা উঠল সাড়ে-তিন হাজার। তাতে কি চারদিন ধ’রে দুর্গাপুজো হয়? প্রতিমা চাই, আলোকসজ্জা চাই, পাত পেয়ে খাওয়া-দাওয়া চাই, এসব খরচ কে জোগাবে? তার জন্য তো রয়েছে স্যুভেনির! অন্যান্য বারোয়ারি পুজোর মতন ফ্ল্যাটবাড়ির পুজো উপলক্ষেও ছাপা হয় স্যুভেনির, তাতে দু-একটা এলেবেলে লেখার সঙ্গে থাকে বেশ কয়েক পাতা বিজ্ঞাপন। ফ্ল্যাটবাড়ির সাহেবদের মধ্যেই পাওয়া যায় কোন কোম্পানির জোনাল ম্যানেজার বা পি. আর. ও. বা সিনিয়র এক্সিকিউটিভ, তাঁরা নিজেদের প্রতিপত্তি খাটিয়ে জোগাড় ক’রে দেন এইসব বিজ্ঞাপন। এছাড়াও যদি দেখা যায় ফ্ল্যাটবাড়ির পুজোতে প্রসাদের সঙ্গে-সঙ্গে একটা ক’রে ভালো কোম্পানির আইসক্রিমও দেওয়া হচ্ছে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। তাহ’লে বুঝতে হবে, ঐ-বাড়িতে ঐ আইসক্রিম কোম্পানির সেল্স ম্যানেজার থাকেন, তিনি তাঁর কোম্পানির কমপ্লিমেন্টসহ একশো-দুশো আইসক্রিমের বাক্স দাতব্য করেছেন।
মানুষের আচরণবিধি নিয়ে কয়েকখানা সহজপাঠ্য বই লিখেছেন যে ডেসমণ্ড মরিস তিনি ঠিকই অনুধাবন করেছেন যে, যে-মনোবৃত্তি নিয়ে একজন মানুষ একটা দেশের রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রী হবার জন্য প্রতিযোগিতায় নামে, ঠিক সেই একই মনোবৃত্তি নিয়ে একজন মানুষ পাড়ার সাঁতার ক্লাবের প্রেসিডেন্ট হ’তে চায়। অর্থাৎ ট্রাইবাল চিফ হবার বাসনা। ফ্ল্যাটবাড়ির পুজো কমিটির প্রেসিডেন্ট বা সেক্রেটারি যাঁরা হন, তাঁরা প্রথমে খুব না-না-না-না বলেন, হাস্যময় বিরক্তি দেখিয়ে বলেন, আরে, আমার ওপর আবার এসব দায়িত্ব চাপানো কেন? আমার কত কাজ। কিন্তু মনে-মনে তাঁদের ঐ-পদাভিলাষ থাকে ঠিকই, কারণ প্রেসিডেন্ট বা সেক্রেটারি হবার পর তাঁদের গলার আওয়াজ বদলে যায়! অর্থাৎ গতকাল পর্যন্ত যিনি ছিলেন .মিঃ ব্যানার্জি বা মিঃ দাশগুপ্ত, আজ থেকে তিনি হয়ে গেলেন এই গ্রামটির মোড়ল।
অবিশ্বাস্য ব্যাপার, এইসব সাহেবদের বাড়িতে এখনও ধুতি থাকে? ট্রাউজার্স ও হাওয়াই শার্ট এখন আমাদের জাতীয় পোশাক। আধা-সাহেবরা গরমকালেও অফিসে যান কোট-টাই প’রে। বাড়িতে হাল্কাভাবে থাকবার সময় পাজামা—পাঞ্জাবি। আজকাল পুজোমণ্ডপে পা-জামা ও প্যান্টের অবাধগতি, কেউ আপত্তি করেনা। কিন্তু ফ্ল্যাটবাড়ির পুজোয় কোন-কোন পাক্কা সাহেবকে দেখা যায় ধুতি প’রে ব’সে থাকতে। রীতিমতন কুঁচোনো ধুতি, ধাক্কা দেওয়া পাড়! মেমসাহেবরাও কেউ-কেউ গরদের শাড়ি বার ক’রে ফেলেন! মুখমণ্ডলে লিপস্টিকসহ প্রসাধন, অঙ্কিত ভুরু, শিঙ্গল ক’রে কাটা চুল এবং লালপেড়ে গরদের শাড়ি পরা এই নতুন ভক্তিমতীদের ভারি চমৎকার দেখায়!
আরও নতুন-নতুন বিস্ময়ের ব্যাপার ঘটে। যে লেডি-ডাক্তারটিকে সারা বছর মনে হয় খুব গম্ভীর কিংবা অহংকারী, এই পুজোর সময় আবিষ্কৃত হ’ল, তিনি খুব সুন্দর আলপনা দিতে পারেন। কিংবা যে মহিলা জীবনে কোনদিন রান্নাঘরে ঢোকেননা, তিনি যে এমন নিখুঁতভাবে শসা কাটতে জানেন, তাই বা কে জানত! প্রদীপ জ্বালবার সলতে পাকিয়েছেন কে? যিনি মন দিয়ে চন্দন ঘষছেন, তিনিই কুকুর নিয়ে ঝগড়া করেছেন ক’দিন আগে?
পাড়ার বারোয়ারি পুজোয় পাতা পেড়ে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা থাকেনা। কিন্তু ফ্ল্যাটবাড়ির পুজোয় চারদিন সব পরিবারে রান্না বন্ধ। ক্যাটেরার নয়, ভিয়েন বসিয়ে একতলাতেই হচ্ছে রান্নাবান্না তারপর সবাই মিলে পংক্তিভোজন। পুজোটা সারা হয়ে যায় খুব দ্রুত, কোনরকমে একজন রোগা পুরুতকে ধ’রে আনা হয় রাস্তা থেকে, সেই পুরুতরাও জানে, এইসব বাড়ির পুজো যত সংক্ষেপে সারা হবে, ততই উদ্যোক্তারা খুশি হবেন। এক বর্ণও সংস্কৃত মন্ত্র না-ব’লে শুধু অং-বং-চং ব’লে গেলেও এইসব ইঙ্গ-বাবুরা কোন ভুল ধরতে পারবেনা। পুজো উপলক্ষে মেলামেশা আর খাওয়া-দাওয়াটাই আসল।
পাশাপাশি যাঁরা খেতে বসেন তাঁরা মনের দিক থেকেও একটু কাছাকাছি চ’লে আসেন। পুজোয় প্রথম দিনে মিঃ চ্যাটার্জি মিঃ দাশগুপ্তকে ডেকে কথা বলেন, মিসেস ভাদুড়ী যেচে আলাপ করেন মিসেস বোসের সঙ্গে। তারপর এইসব মিস্টার আর মিসেসের খোলস থেকে বেরিয়ে আসে এক-একটি নাম, অমলবাবু বা বিমলবাবু, শ্রাবণী বা কাবেরী। ক্রমে বাবুটাও খ’সে যায়, আপনি থেকে কেউ—কেউ নেমে আসে তুমিতে। গর্জন তেল মাখা মা দুর্গার হাসি-হাসি মুখখানি এইসব দেখে আর ভাবে, সব তো ঠিকঠাক আগের মতনই আছে।
৫
প্রেমের সঙ্গে ধূপকাঠির কী সম্পর্ক? কলকাতার কোন প্রেমিক যদি তার প্রেমিকার সঙ্গে গঙ্গার ঘাট বা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনের মাঠে কিংবা বালিগঞ্জ লেকে নিভৃতে কিছুটা সময় কাটাতে চায়, তবে তাকে দু-এক প্যাকেট ধূপকাঠি কিনতে হবেই। প্রেমিকার বাহু ছুঁয়ে আবেগ জড়িত কোন কথার ঠিক মাঝখানে হঠাৎ একটি ছেলে এসে হাজির হবে। সে প্রথমে পাঁচ প্যাকেট ধূপকাঠি বিক্রি করবার চেষ্টা করবে। যদি তাকে বলা হয় যে ধূপকাঠির কোন দরকার নেই তাতে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবেনা। তখন সেই ছেলেটি একটানা কথা ব’লে যাবে, সে একজন বেকার যুবক, তার বাড়িতে ছোটো-ছোটো ভাই-বোন আছে, বাবা অসুস্থ ইত্যাদি! সন্ধেবেলা গঙ্গার ঘাটে কিংবা নিরিবিলি পার্কে বান্ধবীর পাশে ব’সে এইধরনের কথাবার্তা শুনতে কার ভালো লাগে? সুতরাং এক প্যাকেট অন্তত ধূপকাঠি কিনে তাকে বিদায় দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।
এর পরে আসবে অপেক্ষাকৃত একটি কম বয়সী ছেলে। সে বিক্রি করে টফি-লজেন্স-চিউইংগাম। সবসময় সবকিছু খাওয়ার মেজাজ থাকেনা মানুষের। ধরা যাক্, প্রেমিকার সঙ্গে প্রেমিকের কোন এক তৃতীয় ব্যক্তিকে নিয়ে ভুল বোঝাবুঝি চলছে, এইসময় কি প্রেমিক তার প্রেমিকাকে বলতে পারে, এই নাও, একটা টফি খাও। চিউইংগাম চিবোবার সময় মানুষের মুখের ভঙ্গিটাই এমন হয়ে যায় যে তখন কোন সীরিয়াস কথা বলা যায়না। কিন্তু টফি-চিউইংগাম বিক্রেতা বালকটিকে প্রত্যাখ্যান করবার উপায় নেই। কারণ তারও একটা করুণ গল্প আছে। যতক্ষণ-না তার কাছ থেকে কিছু কেনা হবে, ততক্ষণ সে স্থান ত্যাগ করতে চাইবেনা।
সেই ছেলেটিকে বিদায় করবার পরেই আসবে বাদামওয়ালা। চিনেবাদাম খেতে কারুরই আপত্তি থাকার কথা নয়। কেনা হ’ল এক ঠোঙা বাদাম। কিন্তু সেই বাদাম ফুরোতে-না-ফুরোতেই এসে হাজির হবে আর-একজন বাদামওয়ালা। তাকে যদি বলা হয়, এই তো একটু আগেই বাদাম কিনেছি। তাতেও কিন্তু সে চ’লে যাবেনা। সে বলবে, ওর কাছ থেকে কিনেছেন, আমার কাছ থেকে কিনবেননা কেন? আমি খুব গরিব, চিনেবাদাম বিক্রি ক’রে কোনরকমে সংসার চালাচ্ছি…। এর গল্প অনেক বেশি লম্বা, সুতরাং এর কাছ থেকেও কিনতে হবে আর-এক ঠোঙা বাদাম।
এরপর একজন ঝাল-মুড়িওয়ালাও আসতে পারে। কয়েকজন ভিখিরি তো আসবেই। ভিখিরিরা জানে, প্রেমিক-প্রেমিকার সামনে দাঁড়িয়ে থেকে তাদের কথা বলায় বাধা সৃষ্টি করলে ভিক্ষে পাওয়া যাবেই। অনেক প্রেমিক, অন্য সময় ভিক্ষে না-দিলেও, প্রেমিকার সামনে উদার সাজবার জন্য এক টাকা দু-টাকা ভিক্ষে দেয়।
কিছুই চায়না, এমন কিছু লোকও বিরক্ত করতে আসে। এরা হ’ল বেকার ছেলেদের দল, যাদের কোন মেয়ে-বন্ধু নেই। মেয়েরাও আজকাল অনেকেই বেকার হয় কিন্তু দল বেঁধে ঘুরে বেড়ায়না। বালিগঞ্জ লেকে, কলকাতার ময়দানে কিংবা গঙ্গার ধারে বেকার ছেলেরা ঘুরে বেড়ায়, কোথাও কোন প্রেমিক-প্রেমিকাকে ঘনিষ্ঠ ব’সে থাকতে দেখলেই তারা সেখানে গিয়ে দাঁড়ায়। তারা জোরে জোরে কথা বলতে শুরু করে। ক্রমেই ঈর্ষা ও লোভে তারা সীমা ছাড়িয়ে যায়। মেয়েদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ে তারা কুৎসিত আলোচনা শুরু করে। এমনকি তারা অনেকসময় কাছের মেয়েটিকে উদ্দেশ ক’রেই কদর্য ইঙ্গিত করতে আরম্ভ করে।
এইসব ক্ষেত্রে প্রেমিকটি রাগে ফুঁসতে থাকলেও বিনা প্রতিবাদে তার সঙ্গিনীকে নিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে যাওয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। প্রতিবাদ করতে গেলেই ওরা সত্যিকারের বিপদে প’ড়ে যাবে। বেকার যুবক বা তথাকথিত মাস্তানরা তো ঐরকম কিছুই চায়। এদের শিভালরি জ্ঞান তো নেই—ই, এরা একসঙ্গে চার-পাঁচজন মিলে একজনকে আক্রমণ করতেও দ্বিধা করেনা। একজন প্রেমিক তার প্রেমিকার সম্মান রক্ষা করার জন্য চার-পাঁচজন মাস্তানকে শায়েস্তা ক’রে দিচ্ছে, এরকম শুধু সিনেমাতেই দেখা যায়। বাস্তবে আমরা এরকম অসম সাহসী ও বলশালী প্রেমিকদের দেখতে পাইনা। কিংবা সেরকম বলশালী যুবকেরা পার্কে কিংবা গঙ্গার ঘাটে কোন মেয়ের সঙ্গে প্রেম করার মতন হাল্কা ব্যাপারে সময় নষ্ট করেনা।
অচেনা মেয়ের প্রতি খারাপ উক্তি ক’রে কিংবা দুজন প্রেমিক-প্রেমিকাকে বিবক্ত ক’রে এইসব মাস্তানরা কী আনন্দ পায়? এককালে যারা পাড়ার গুণ্ডা বা মাস্তান হিসেবে পরিচিত ছিল, পরে বিয়ে-টিয়ে ক’রে কোনরকম চাকরি পেয়ে ঘর-সংসারী হয়েছে, এরকম দু-একজনকে আমি চিনি। নিজের বাড়িতে এরা অত্যন্ত রক্ষণশীল। এরা নিজেদের স্ত্রীদের কখনও একলা বাড়ি থেকে বেরুতে দেয়না। স্ত্রীদের সঙ্গে নিয়ে সিনেমা-থিয়েটারেও যায়না। পাড়ার কেউ এদের কারুর স্ত্রীর সঙ্গে কোন কথা বললেই এরা চ’টে যায়। মেয়েদের এরা নিছক গৃহপালিত প্রাণী ব’লে মনে করে। এখনও। এ-দেশের অধিকাংশ পুরুষেরই এইরকম মনোভাব।
কিছু-কিছু লোক আছে এই শহরে যাদের জীবিকাই হ’ল প্রেমিক-প্রেমিকাদের ভয় দেখানো।
একটি যুবক ও যুবতী যদি মনের দিক থেকে কাছাকাছি আসে, তবে তারা শারীরিকভাবেও কাছাকাছি আসতে চাইবে, এটা তো খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু কলকাতার অতি জনবহুল শহরে সেরকমভাবে মেলামেশার কোন জায়গাই নেই। পৃথিবীর অনেক দেশে এখন লিভিং টুগেদার বহুল প্রচলিত। আর আমাদের এখানে কোন ছেলে তার ইচ্ছুক বান্ধবীকে একটা চুমু খাওয়ারও সুযোগ-সুবিধে পায়না। শুধু-যে নিরিবিলি জায়গার অভাব তাই-ই নয়, তার ওপর সবসময় প্রেমিক—প্রেমিকাদের ওপর বাজ পাখির মতন নজর রাখছে এই সমাজের রক্ষণশীল মানসিকতা।
নিরুপায় হয়েই কোন-কোন যুবক-যুবতী ময়দানের অন্ধকারে গিয়ে বসে। প্রেমে পড়ার পর এমন একটা সময় আসে, যখন পরস্পরের সান্নিধ্যে তৃতীয় কোন ব্যক্তির দৃষ্টিও সহ্য হয়না। এই শহরের বেশিরভাগ ছেলেমেয়েই হোটেল—রেস্তোরার ব্যয় বহন করতে পারেনা। বাড়িতেও দেখা করার কোন সুযোগ নেই, সুতরাং ময়দানের অন্ধকার ছাড়া আর উপায় কী?
যখন তারা পরস্পরের প্রতি একেবারে বিভোর হয়ে থাকে ঠিক সেইসময় যেন মাটি ফুঁড়ে উঠে আসবে একটা লোক। তার লম্বা-চওড়া চেহারা। নাকের নিচে পাকানো গোঁফ। এসেই সে প্রেমিকটির হাত শক্ত ক’রে চেপে ধ’রে হুকুমের সুরে বলবে, থানায় চলো!
ছেলেটি ও মেয়েটি সহসা এই উৎপাত দেখে ঘাবড়ে যেতে পারেই। তারা জানতে চাইবে, কী তাদের অপরাধ? সেই লোকটি বলবে যে ছেলেটি ও মেয়েটি ঘাসের ওপর শুয়ে যে-কাজটি করছিল, সে-কাজটি বে-আইনী। সেইজন্য তাদের যেতে হবে থানায়। এই কথাটি শুনে মেয়েটি লজ্জিত ও অপমানিত বোধ করবে এবং ছেলেটি রেগে উঠে বলবে, মোটেই তারা সেরকম কিছু বে-আইনী কাজ করেনি। তারা শুয়ে থাকেনি। তারা পাশাপাশি ব’সে গল্প করছিল শুধু। লোকটি তখন বলবে, ঠিক আছে, কী করছিলেন, তা থানার বড়বাবুর কাছে গিয়েই বলবেন। এখন চলুন! বেশি গোলমাল করলে আমি হুইস্ল বাজাব, আরও পুলিশ আসবে।
এরপর লোকটি হুইল মুখে দিয়ে ছেলেটির হাত ধ’রে টানাটানি শুরু করবে। মেয়েটির চোখে জল আসবে। তাদের চোখে ভেসে উঠবে থানা, জেল, রাতে বাড়ি না-ফেরা, খবরের কাগজে তাদের ঘটনা নিয়ে রসালো মন্তব্য ইত্যাদি। ছেলেটি তখন তেজ ভুলে গিয়ে অনুনয়বিনয় ক’রে বলবে, ভুল হয়ে গেছে, এবারকার মতন ছেড়ে দিন!
ছাড়া ওরা পাবে, তার আগে ছেলেটির পকেটের সব টাকা-পয়সা তুলে দিতে হবে ঐ-লোকটির হাতে।
আমার নিজেরই একবার এরকম অভিজ্ঞতা হয়েছিল। সত্যি কথা বলতে কী, আমি ময়দানে ব’সে আমার বান্ধবীর পিঠে হাত রেখে তাঁকে একটি চুম্বন করার জন্য কাকুতি-মিনতি করছিলুম, তিনি রাজি হচ্ছিলেননা, সেই মুহূর্তে সেই যমদূতের আবির্ভাব। আমার বান্ধবীর সম্মান রক্ষা করার জন্যই আমার পকেটের সবকিছু তাকে দিয়ে নিষ্কৃতি পেতে হয়েছিল।
এর কয়েক বছর পরে কয়েকজন পুলিস অফিসারের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়। তাঁদের এই ঘটনাটা বলায় তাঁরা খুব হেসেছিলেন। তাঁরাও শুনেছেন যে ঐরকম কয়েকটি লোক পুলিস সেজে ময়দানে প্রেমিক-প্রেমিকাদের ভয় দেখায়। ওদের জব্দ করার খুব সহজ রাস্তা আছে। ওরা এসে ধরলেই বলতে হয়, হ্যাঁ, চলো থানায়। এক্ষুণি চলো! তখন ওরাই ভয় পেয়ে পালিয়ে যায়!
এই কথা শোনার পর আমি আবার ময়দানে আমার বান্ধবীকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে বসেছি সেই লোকটিকে ধরার জন্য। কিন্তু সে আমার কাছে আর কোনদিন আসেনি। ওরা ঠিক মানুষ চিনতে পারে।
৬
আমি মাঝে-মাঝে একটা বাড়িতে যাই, যে-বাড়িতে দাস-দাসীর সংখ্যা একশোর বেশি। গাড়ি আছে ষাট-সত্তরটা। ড্রাইভার হবে অন্তত পঞ্চাশজন। দারোয়ান পাঁচ—ছজন। সেই বাড়ির গেটে সারা রাত আলো জ্বলে।
না, এটা কোন বিরাট বড়লোকের বাড়ি নয়। শোনা যায়, ওয়ারেন হেস্টিংস কিংবা ফিলিপ ফ্রান্সিসের একশোর বেশি দাস-দাসীর প্রয়োজন হ’ত। সেরকম
বিলাসী বড়লোকদের আজকাল আর অস্তিত্ব নেই। আমি যে-বাড়িটাতে যাই সেটা একটা দশ তলা ফ্ল্যাট বাড়ি।
সেই বাড়িটিতে সত্তরটি অ্যাপার্টমেন্ট আছে। অর্থাৎ সত্তরটি পরিবার। আমাদের দেশের অনেক গ্রামেই এর চেয়ে জন্যসংখ্যা কম। অর্থাৎ এই বাড়িটিকেও একটি কংক্রিটের তৈরি গ্রাম বলা যায়। কিন্তু গ্রামের পরিবারগুলি থাকে অনেকখানি আকাশের নিচে। কলকাতার এইসব বাড়ির মানুষের সঙ্গে আকাশের কোন সম্পর্ক নেই।
কলকাতায় এরকম বড় বাড়ি আগে মাত্র কয়েকটি ছিল। গত দশ বছরে এরকম বাড়ি গজিয়ে উঠেছে অসংখ্য। শুরু হয়েছে নতুন একধরনের জীবনযাত্রা। লিফট দিয়ে ওঠার সময় লক্ষ করি, ভেতরে যে পাঁচ-ছজন নারী-পুরুষ দাড়িয়ে আছে, তারা কেউ কারুর সঙ্গে কথা বলেনা, প্রত্যেকে নিঃশব্দে নিজের—নিজের নাক দেখছে। মনে হয়না এটা কোন বসত বাড়ি, মনে হয় যেন অফিস।
একই ছাদের নিচে বাস করেও অনেকেই অনেকের নাম জানেনা। আটতলার একজন লোককে খুঁজতে গিয়ে আমি একবার ভুল ক’রে সাততলার একটি অ্যাপার্টমেন্টের দরজায় বেল দিয়েছিলুম। দরজা খুলে একজন ভদ্রলোক বেরিয়ে এসে ইংরেজিতে আমায় জিজ্ঞেস করলেন, কী চাই? আমি আমার বন্ধুর নাম ব’লে জিজ্ঞেস করলুম, উনি কোন্ ফ্লোরে থাকেন বলতে পারেন? ভদ্রলোক দরজা বন্ধ ক’রে দিতে-দিতে সংক্ষেপে জানালেন, লিটম্যানকে জিজ্ঞেস করুন!
আমার বন্ধুটি একটি বেশ বড় কম্পানিতে চাকরি করে। সেই কম্পানি থেকে তাকে এই অ্যাপার্টমেণ্ট দিয়েছে। আটতলার ওপর আলো হাওয়ায় চমৎকার। এত উঁচু থেকে কলকাতা শহরটাকেও বেশ ভালোই দেখায়। বিশেষত সন্ধের পর। মনে হয় নিউ ইয়র্ক, লণ্ডনের সঙ্গে কোন তফাৎ নেই। চারদিকে এরকম উঁচু—উঁচু বাড়ি, দূরের বাড়িগুলিকে মনে হয় ঝলমলে জাহাজের মতন। অন্তত একশোটা জানলায় আলো জ্বলছে। অবশ্য হঠাৎ লোড়শেডিং হ’লে পুরো অঞ্চলটাই আবার গ্রাম হয়ে যায়।
কোন-এক ছুটির দিনের সকালে ঐ-অ্যাপার্টমেন্টে ব’সে চা খাচ্ছিলুম। বন্ধুপত্নী এই নতুন বাড়ি পেয়ে খুব খুশি। অনেকরকম প্রশংসা করছিলেন। দক্ষিণ খোলা বাড়িতে থাকলে নাকি স্বাস্থ্য ভালো হয়। হঠাৎ দরজার বেল বেজে উঠলে বন্ধুটিই দরজা খুলে দিল। চাঁদার খাতা হাতে তিন-চারটে ছেলে দাঁড়িয়ে। বন্ধুটি হাসতে-হাসতে ফিরে এসে স্ত্রীকে বললেন, ছেলেরা এসে গেছে, ওদের চাঁদাটা দিয়ে দাও।
আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলুম, এত উঁচুতেও চাঁদা আদায়কারীরা ওঠে? আমার ধারণা ছিল, মশা, মাছি, ভিখিরি আর চাঁদা আদায়কারীরা এত উঁচুতে উঠতে পারেনা!
বন্ধুটি বলল, তোমার ধারণা ভুল। মশারাও আধুনিক জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। অ্যাসট্রোনটদের কায়দায় তারাও লিফট দিয়ে উঠে আসে ওপরে। সাধারণ ভিখিরিরা আসতে পারেনা বটে, তবে রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুর ছদ্মবেশে কিংবা ইংরেজিতে লেখা আবেদনপত্র নিয়ে মাদ্রাজি বোবা আসে। আর এই যে চাঁদা আদায় করতে এসেছে, এরাও সাধারণ, রাস্তার ছেলে নয়। এরা সব এ—বাড়িরই ছেলে, এ-বাড়িতেই পুজো হবে সেইজন্য সব ফ্ল্যাট থেকে চাঁদা তুলছে।
বন্ধু পত্নী জিজ্ঞেস করল, কত দেব?
বন্ধুটি বললো, দাও, তিরিশ টাকা দিয়ে দাও!
আমি আবার অবাক। আমার বন্ধুটি কট্টর মার্কসবাদী এবং নাস্তিক। কোন পুজো-টুজোর ব্যাপারে কোনদিন ওর উৎসাহ দেখিনি। সে দিচ্ছে তিরিশ টাকা চাঁদা?
পরের সপ্তাহে গিয়ে দেখলুম, আমার বন্ধুটির অ্যাপার্টমেন্টে একটা নতুন টি. ভি. সেট বসানো হচ্ছে। এর আগে আমার বন্ধুটির মুখে টি. ভি.র প্রচুর নিন্দে শুনেছি। সাহেবি কায়দায় সে টি. ভি.-কে বলত ইডিয়ট বক্স।
বোধহয় আমার মনের কথা বুঝতে পেরেই বন্ধুটি বললেন, এসব বাড়িতে থাকলে সবার সঙ্গে মানিয়ে চলতে হয়। এখানে যদি আমি আমার নিজস্ব মতামত ফলাতে যাই, তাহ’লে শান্তিতে থাকা কঠিন।
বন্ধুটি আমায় দেখে কাঁধ শ্রাগ্ ক’রে বলল, আমার একদম ইচ্ছে ছিলনা, কিন্তু আমার ছেলের জন্য। ও নিচের একটা ফ্ল্যাটে খেলাধুলোর প্রোগ্রামগুলো দেখতে যেত, ওদের কুকুরটা আমার ছেলেকে কামড়ে দিয়েছে। আর ওকে সেখানে পাঠানো যায়না।
আমি বললুম, তাছাড়া আজকাল টি. ভি. না-থাকলে বাড়িতে কাজের লোক কিংবা রান্নার লোক টেকেনা। না-রাখলে চলে কী ক’রে—।
ঐ-বাড়িতে যাতায়াত ক’রে আমি এই নতুন জীবনযাত্রার ছবিটি ক্রমশ বেশ ভালো ক’রে বুঝতে পারলুম। এইসব বাড়িতে নানান জাতি ও নানান ভাষার লোকজন থাকে। কলকাতা শহরে বাঙালিরা এর আগে এমনভাবে অন্য প্রদেশের লোকদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকেনি। কলকাতায় বিভিন্ন পাড়ায় বিভিন্ন প্রদেশের লোকদের আলাদা-আলাদা বসতি আছে বটে, কিন্তু সেখানে বাঙালিদের সঙ্গে তাদের বিশেষ মেলামেশা নেই।
এইসব বড় অ্যাপার্টমেন্ট হাউসে বয়স্করা নিজেদের মধ্যে বেশি মেলামেশা না-করলেও বাড়ির শিশুরা ঠিকই মেশে। বাচ্চারা পরস্পরের সঙ্গে আলাপ পরিচয়ের জন্য অন্য কারুর মুখাপেক্ষী নয়, তারা নিজেরাই ভাব ক’রে নেয়। বাড়ির সামনের জায়গাটায় কিংবা সিড়ির ল্যান্ডিং-এ আমি রোজই নানা বয়েসের বাচ্চা ছেলেমেয়েদের খেলা করতে দেখি। একটু বড়ো ছেলেমেয়েরা ইংরেজিতে কথা বলে, আর একেবারে বাচ্চারা যে নিজেদের মধ্যে কীভাবে ভাব বিনিময় করে তা তারাই জানে।
সিঁড়ি দিয়ে একটি যুবক ও যুবতীকে হাসতে-হাসতে নামতে দেখে আমার মনে হয়, এইরকম বাড়িতে তরুণ ও তরুণীদের মধ্যে প্রেম ও বিয়েও হ’তে পারে নিশ্চই। একই বাড়ির পাত্রপাত্রীর বিয়ে। তারপর যদি বিচ্ছেদ হয় কিংবা বিয়ের আগেই ভালোবাসা ভেঙে যায়, তাহ’লে তখনও ওদের একই বাড়িতে থাকা অসহ্য মনে হবেনা?
একদিন আমি আমার বন্ধুকে বললুম, তোমাদের বাড়ির জীবনযাত্রা দেখলে মনে হয় আধুনিক ইংরেজি নভেলের চরিত্র তোমরা। ভারতীয় মনে হয়না। ইংরেজ—আমেরিকার শহুরে মধ্যবিত্তদের সঙ্গে তোমাদের তফাৎ কী?
বন্ধুটি হেসে বলল, তফাৎ আছে হে! প্রত্যেকটি ফ্ল্যাটের রান্নাঘরে গিয়ে উঁকি মারো। সেখানে গিয়ে দেখবে সবাই ভারতীয় শুধু নয়, বিভিন্ন রাজ্যের আলাদা—আলাদা মানুষ র’য়ে গেছে এখনও
৭
কিছুদিন আগে আমি একটি ধর্মসভায় যোগ দিয়েছিলুম, যোগ দিতে বাধ্য হয়েছিলুম বলা যায়, যদিও সবলে নয়। খুলে বলি।
এক মধ্যাহ্নে আমার কর্মস্থানে এক মুণ্ডিত মস্তক শ্বেতাঙ্গ, ইংরিজিভাষী সাধুর আবির্ভাব হয়। সঙ্গে একটি সপ্রতিভ চেহারার বাঙালি যুবক। যুবকটি হাসি মুখে আমাকে দাদা ব’লে সম্বোধন ক’রে এবং পরিচিতের ভঙ্গিতে, কী খবর, কেমন আছেন, অনেক দিন দেখা হয়নি ইত্যাদি দিয়ে কথা শুরু ক’রে এইসব ক্ষেত্রে আমিও কী খবর ভালো তো, হ্যাঁ, অনেকদিন পর দেখা এইসব আলগাভাবে বলতে—বলতে যুবকটির সঙ্গে কবে, কোথায় পরিচয় হয়েছিল এবং তার নাম কী মনে করবার চেষ্টা করি। কিছুই মনে পড়েনা। তার মুখমণ্ডলের সামান্য ছাপও আমার স্মৃতিতে খুঁজে পাইনা। তাতে অবশ্য কিছু আসে-যায়না। কথাবার্তা চালিয়ে যাওয়া যায়।
সাধুটিও তরুণ বয়স্ক, ইনি আন্তর্জাতিক কৃষ্ণচৈতন্য সংস্থার একজন ছোটোখাটো কর্মকর্তা। মায়াপুরে এদের হেড অফিস, কলকাতা সমেত পৃথিবীর কয়েকশো বড়ো-বড়ো শহরে এদের শাখা কার্যালয় ও ভজনালয় আছে। এই কৃষ্ণচৈতন্য সম্প্রদায় সম্পর্কে আমি খুব বেশি কিছু জানিনা, আবার একেবারে অজ্ঞও নই, আমি মায়াপুর দর্শন করেছি, ভারতের বাইরে দু-একটি শহরে এদের কার্যকলাপ দূর থেকে লক্ষ করেছি। এঁদের সম্পর্কে আমার কিছুটা কৌতূহল, কিছুটা কৌতুক এবং খানিকটা শ্রদ্ধার ভাবও আছে। যদিও এঁদের সম্পর্কে কাঁধ ঘেঁষাঘেঁষির আকাঙ্ক্ষা আমার কখনও জাগেনি। যাই হোক্, এঁরা আমার কাছে এসেছেন কেন?
সাধুটি বেশ বিনীত এবং নম্রভাষী। তিনি জানালেন যে কলকাতায় তাঁরা তিনদিন ব্যাপী এক আলোচনা সভার আয়োজন করেছেন, তাতে আমাকে অংশ গ্রহণ করতে হবে। শুনে তো আমি আকাশ থেকে পড়লুম। ব্যাংক কর্মচারিদের বার্ষিক জলসা। পাড়ার ক্লাবের আবৃত্তি প্রতিযোগিতা, মফস্বলের সংস্কৃতি উৎসব ইত্যাদিতে নৈবেদ্যর ওপর বাতাসা হবার জন্য মাঝে-মাঝে আমার কাছে উপরোধ আসে, আগে অনেকবার ঢোক গিলতে হয়েছে, ইদানিং পারতপক্ষে এড়িয়ে যাই কিংবা পলায়ন করি। কিন্তু ধর্মীয় সংস্থা থেকে আমার কাছে কোনদিন ডাক আসেনি। তাহ’লে কি আমার চরিত্রের এতই অধঃপতন হয়েছে যে পুণ্যাত্মারা আমাকে শেষে উদ্ধার করবার জন্য এগিয়ে আসছেন?
আমি হাত জোড় ক’রে আমার অক্ষমতা জানালুম। কিন্তু সাধুটি নম্ৰ হ’লেও জেদি এবং নাছোড়বান্দা। তার উচ্চারণে আমেরিকার টান, অর্থাৎ বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করলেও তিনি জাতীয় চরিত্র হারাননি। কোন ব্যাপারেই এঁরা বিমুখ হতে জানেননা। সাধুটি আমাকে বোঝাতে চাইলেন যে আলোচনাসভাটি নিছক ধর্মীয় নয়। ভারতের দারিদ্র্য দূর করার উপায় খুঁজে বার করাই মুখ্য উদ্দেশ্য, সমাজসেবায় একটি সার্থক পথ নির্ণয় এবং মানুষের আত্মিক মুক্তি ও ইহজাগতিক সুখের সমন্বয়কার্য সেদিনের বিষয়বস্তু, ‘মানুষের সেবাই কি ঈশ্বর সেবা?’
আমি বললুম, অনাথদের উদ্দেশ্য বেশ শুভ মনে হচ্ছে, কিন্তু আমায় ডাকছেন কেন? আমি সমাজসেবক নই, ধর্মবিশ্বাসী নই, ভালো বক্তাও নই, সুতরাং সব দিক থেকেই আমি অনুপযুক্ত। সাধুটি বললেন, তাঁরা সমাজের সব দিকেরই প্রতিনিধিদের মতামত চাইবে, মন্ত্রী, আমলা, উপাচার্য, চিকিৎসক, বিচারক, ব্যবসায়ী, সবাই থাকছেন, সাহিত্যজগৎ থেকেও একজন প্রতিনিধি চাই। আমার চরিত্রের একটা প্রধান দোষ, আমি যথাসময়ে দৃঢ়ভাবে ‘না’ বলতে পারিনা। একটা অনাবশ্যক ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে যাচ্ছি জেনেও আমার প্রত্যাখ্যান যথেষ্ট জোরালো হ’লনা, আমাকে নিমরাজি অবস্থায় ফেলে রেখে ওঁরা বিদায় নিলেন, যাবার আগে বাঙালি যুবকটি আমাকে প্রচুর ধন্যবাদ জানাতে ভুললেননা।
অন্তর্বর্তী দিনগুলিতে আমি বেশ ফাঁপরের মধ্যে রইলুম। আমাকেই ওরা বেছে নিলেন কেন? সাহিত্যজগতে আমার চেয়ে যোগ্যতর প্রতিনিধি ভুরি-ভুরি। অনেক খ্যাতিমান লেখক ধর্মপ্রাণ, কেউ-কেউ ব্যক্তিগত জীবনে ধর্ম প্র্যাকটিস করেন তা—ও আমি জানি। যে বাঙালি যুবকটি মধ্যবর্তী হয়ে এসেছিল তার পরিচয় আমার কিছুতেই মনে পড়ছেনা।
এযাবৎ আমি রামকৃষ্ণ মিশন সমেত সমস্ত ধর্মপ্রতিষ্ঠান থেকে সসম্ভ্রমে দূরে থেকেছি। সাধারণভাবে সাধুদের সম্পর্কে আমার একটা সমীহের ভাব আছে, তাঁরা ঘরছাড়া বিবাগী ব’লে। প্রাতিষ্ঠানিক সাধুদের সম্পর্কে আমার কোন আগ্রহ নেই। বিদ্যাসাগর বেদান্তকে বলেছেন ভ্রান্ত দৰ্শন।
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বেদকে কোন ধর্মগ্রন্থ ব’লে স্বীকার করেননি, বলেছেন একখানি উৎকৃষ্ট কাব্যসংকলন মাত্র, পলগ্রেভের ‘গোল্ডেন ট্রেজারি’র মতন। আমিও এই ধারায় বিশ্বাসী। মহাভারত আমি একটি উৎকৃষ্ট উপন্যাস হিসেবে বারংবার পড়ি, শ্রীম লিখিত ‘শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত’ যেমন চমৎকার সুখপাঠ্য একটি বই, দু-একটি ভুল তথ্য ও পৌনঃপুনিকতা থাকা সত্ত্বেও। বাইবেলের দুটি খণ্ড, কোরান ও হাদিস কয়েকবার প’ড়ে আমি বেশ কিছু আকর্ষণীয়, কাব্যময় পরিচ্ছেদ পেয়েছি, কিন্তু কোন গভীর উপলব্ধি হয়নি। সবক’টি ধর্মীয় দর্শন আমার কাছে গ্রামীণ ও সংকীর্ণ মনে হয়, আধুনিক মানুষের জীবনযাপনে এইসব ধর্মের প্রাদেশিকতা টেনে আনা একেবারেই অবান্তর।
নির্দিষ্ট দিনে আমি অকুস্থলে উপস্থিত হলুম। সাধুরা গাড়ি পাঠাতে চেয়েছিলেন, আমি প্রত্যাখ্যান করেছি, কারণ অপরের বাহনের ওপর নির্ভর করলে স্বাধীনভাবে প্রস্থান করা যায়না। একটি ভাড়া-করা মঞ্চ তখনও সাজানোর পালা চলছে। পশ্চাৎপটে দামি মখমলের ওপর লেখা সার্ভিস টু ম্যান ইজ সার্ভিস টু গড। চতুর্দিকে নানান বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, ভি. ডি. ও. ক্যামেরা স্থাপিত হচ্ছে, শোনা গেল পুরো অনুষ্ঠানটি চিত্রায়িত ক’রে তার ক্যাসেট পাঠানো হবে রাজীব গান্ধী সমেত শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের কাছে।
শ্রোতাদের আসনে সাধুসন্ন্যাসীর বেলি, শাড়ী পরা বিদেশী ললনা ও মুণ্ডিত মস্তক, শিখাধারী মার্কিন যুবকরা রয়েছেন অভ্যর্থনায়। মাটির পাত্রে গরম-গরম হালুয়া বিতরিত হচ্ছে উদারভাবে।
কিছু-কিছু ভারতীয় মাথা কামিয়ে, গেরুয়া প’রে এই সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। মঞ্চে ওঠার আগে এরকম একজন দিশি সাহেব-সাধুর সঙ্গে আমার কথাবার্তার সূত্রপাত হ’ল। ইনি অবাঙালি, ইংরেজি ভাষায় বেশ রপ্ত। নিজের থেকেই জানালেন যে চাকরি-বাকরি ছেড়ে এই ধর্ম আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন জীবনের অর্থ খোঁজার জন্য। আমি জিজ্ঞেস করলুম, খুঁজে পেয়েছেন? তিনি বললেন, খুঁজে চলেছি, এ-খোঁজার তো শেষ নেই।
জীবনের অর্থ খোঁজার জন্য নিরামিষ খাওয়া ও গেরুয়া ধারণের কী প্রয়োজন তা আমার বোধগম্য হয়না। আইনস্টাইন, বার্ট্রান্ড রাসেল কী জীবনের অর্থ খোঁজেননি? খোঁজেননি জীবনানন্দ দাশ কি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়? যে অভিজ্ঞ চাষী খরার সময় গাছতলায় দাঁড়িয়ে শূন্য মাঠের দিকে শূন্যতর দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে, সে-ও কি জীবনের অর্থ খোঁজেনা?
সাহেবদের অনুষ্ঠান হ’লেও কলকাতার মাটিতেই তো, তাই বাঙালি কায়দায় মিনিট পনেরো কুড়ি পরে শুরু হ’ল। সভাপতি একজন মার্কিনী অধ্যাপক, এঁরও মাথায় টিকি এবং গায়ে সিল্কের গেরুয়া। ইনি আন্তর্জাতিক এই সংস্থার বড়ো গোছের একজন চাঁই। পরিচিতের আরও জানানো হল, ইনি একজন বেদান্ত—বিশেষজ্ঞ। আলোচকদের মধ্যে রয়েছেন হাইকোর্টের একজন প্রাক্তন বিচারপতি, ইনি উদারচেতা মুসলমান হিসেবে খ্যাত, আর লায়ন্স ক্লাবের দুজন কর্মকর্তা, পেশায় উচ্চশ্রেণীর ব্যবসায়ী, একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী উপস্থিত এবং আমি। প্রথমে সভাপতির মূল ভাষণ, তারপর প্রশ্নোত্তর, সবকিছুই ইংরেজিতে।
সভাপতির ভাষণের প্রথম খণ্ডে নতুন কথা কিছুই শোনা গেলনা। পাকা অধ্যাপকের আ-ভাঙা বাক্য গড়গড়িয়ে অনেকক্ষণ ব’লে যেতে পারেন, তাতে সারবস্তু কিছু থাক্-না-থাক্। এই সাহেবটি বেদ উপনিষদের মালমশলা ছাত্রদের শোনাবার মতো ক’রে আমাদের দিকে তাকিয়ে যেভাবে বলছিলেন তাতে কৌতুকই উদ্রেক করে। কিন্তু এইসব গুরুগম্ভীর ধর্মসভায় হাসি নিষিদ্ধ।
হ্যাঁ ধর্মসভাই নিশ্চিত। মানুষের সেবার কথা এখানে গৌণ। সভাপতিটির বক্তব্যের সুর অবিকল ধর্মপ্রচারকের মতন। দ্বিতীয়ার্ধে তাঁর উদ্দেশ্য আরও প্রকট হ’ল। তিনি বললেন, জীবজগতের মধ্যে মানুষ শ্রেষ্ঠ প্রাণী। এবং মানুষের এই শ্রেষ্ঠত্ব তখনই চূড়ান্ত হয় যখন সে জড়জগতের বন্ধন কাটিয়ে ঈশ্বরকোটিতে প্রবেশ করে। কর্ম করলে মঙ্গমলয় হয়না যদি-না তাতে বিশুদ্ধ ভক্তি থাকে। আজকের মানুষ এই ভক্তিবাদ থেকে বিচ্যুত। শ্রীকৃষ্ণের যে-প্রেমধর্ম ইত্যাদি ইত্যাদি।
এক ঘণ্টা ধ’রে এরকম বক্তৃতা শোনার ধৈর্য আমার নেই। আমি মঞ্চ, মঞ্চের বাইরের ঘটনা লক্ষ করছিলুম। এই বৈঠকে সাধুদের ঐশ্বর্যের চিহ্ন চোখে না-প’ড়ে উপায় নেই। অধিকাংশ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানই ধনী। এরা বোধহয় আরও ধনী, এদের চাঁদা আসে বিদেশী মুদ্রায়। ধনকুবের হেনরি ফোর্ডের কোন নাতিও নাকি এঁদের সদস্য! সাহেব-সাধুদের সকলেরই অঙ্গে গেরুয়া, তার দামের তারতম্য আছে। না-হয় সিল্ক, কারুর সুতো। বাইরের কাউণ্টারে অতি মূল্যবান কাগজে ছাপা বই বিক্রি হচ্ছে অস্বাভাবিক কম দামে।
ঘরছাড়া এইসব তরুণ-তরুণী কিসের টানে এই অস্বাস্থ্যকর পশ্চিম বাংলায় দিনের পর দিন প’ড়ে আছে তা আমি জানিনা। ওদের দেশে বিজ্ঞান তৈরি ক’রে দিচ্ছে নিত্যনতুন আরাম, সেসব ত্যাগ ক’রে এই স্বেচ্ছানির্বাসন, এর মধ্যে একটা ট্র্যাজিক সৌন্দর্য আছে নিশ্চিত। মাথা ন্যাড়া ক’রে, গেরুয়া ধুতি প’রে কলকাতার রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো, দিনের পর দিন হালুয়া-খিচুড়ি ভক্ষণ, এই সহ্য শক্তি তো ধর্ম জাগাতে পারে? নাকি এ এক যুক্তিহীন উন্মাদনা। আমাদের দেশে অনেকেই এঁদের বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগ ছুঁড়ে দেন। দায়িত্বজ্ঞানহীন উক্তি করা আমাদের ব্যাসন। বিনা প্রমাণে আমি সেরকম কিছু মনে করিনা, তবে দু-চারটে গুপ্তচর এদের মধ্যে ঢুকে পড়তেই তো পারে, তা আশ্চর্য কিছুনা। চীনে যখন পিং-পং খেলার জন্য প্রথমে একটি মার্কিন দল পাঠাবার প্রস্তাব গৃহীত হয়, তখন সি. আই. এ.-র এজেন্টদের মধ্যে অতি দ্রুত পিং-পং খেলা শিখে নেবার ধুম পড়ে গিয়েছিল।
ভোগবিলাসে বিমুখ হয়ে এককালে রাজার দুলালরা ঘর ছাড়ত। গৌতম বুদ্ধের বাবার চেয়ে হেনরি ফোর্ড নিশ্চিত অনেক গুণ বেশি বড়লোক। সে-কারণটা না-হয় মেনে নেওয়া যায়। সম্প্রদায় গঠন ক’রে তার প্রভাব বিস্তারের যে-চেষ্টা, তার মনস্তত্ত্বটা কী? রাজীব গান্ধীকে কেন এই আলোচনাসভার ক্যাসেট পাঠানো হবে? তা কি এটাই প্রমাণ করবার জন্য যে এই সম্প্রদায় নিছক ধর্মীয়, এর মধ্যে রাজনীতি নেই, দেশের সর্বস্তরের মানুষের মতামত এখানে গ্রাহ্য করা হয়! সরকারি আইনের লম্বা হাত কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে ছোঁয়না। অন্য বক্তারাও খুব ভালো কথা বললেন। মানুষের সেবা তো ভগবানের সেবা বটেই। সব ধর্মের বাণীই এক, মানুষকে ভালোবাসো ইত্যাদি!
এরপরে আমি যদি বলতুম, আমার আর-কিছু বক্তব্য নেই, এবারে শেষ হয়েছে তো, চলুন ওঠা যাক্, তাহ’লে সব ব্যাপারটা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হ’ত। কিন্তু আমার মাথায় একটা দুষ্টুবুদ্ধি চাপল। ভিমরুলের চাকে ছুঁড়ে মারতে ইচ্ছে করল ছোট্ট একটা ঢিল। আমি বললুম, দেখুন মশাইরা, আমার পঞ্চাশ বছর বয়েস হ’ল, এ পর্যন্ত আমি কখনও ঈশ্বরচিন্তা করিনি। ঈশ্বরও নিশ্চয়ই আমাকে নিয়ে চিন্তা করেননি। কিন্তু আমরা দুজনে তো বেশ ভালোই আছি। কেউ কারুর ঝঞ্ঝাটে নেই। আমার ধর্ম-টর্মের কোন বালাই নেই, কিন্তু আমি লোক খারাপনা। চুরি জোচ্চুরি করিনা, কারুকে ঠকাইনা, বরং সাধ্যমতো অপরের উপকার করার চেষ্টা করি! তাহ’লে আপনারা এত ধর্ম-ধর্ম করেন কেন? মানুষের সেবা করার কথা বলবেন, তা বেশ তো, করুন-না; তার মধ্যে আবার ভগবানকে টেনে আনার দরকারটা কী? সে-লোকটা আকাশে বেশ আছে, থাক্-না!
প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই ভগবান আছে, এ আমি বিশ্বাস করিনা। মানুষের পেটে ভগবান হজম করা খুব শক্ত। তাছাড়া প্রশ্ন উঠবে, সেটা কার ভগবান? কোন্ ধর্মের ভগবান? সব ধর্মেই বলেছে মানুষকে ভালোবাসো, এ অতি ঘোর মিথ্যে কথা। সব ধর্মই বলে, শুধু নিজের সম্প্রদায়ের লোকদের ভালোবাসো, অন্যদের ধ’রে পেটাও! পৃথিবীতে এ-পর্যন্ত যত গণ-খুনোখুনি হয়েছে সবই তো পবিত্র ধার্মিকদের ব্যবস্থাপনায়। মানুষের ভালোবাসা অত সহজ নয়! মোক্ষ, মুক্তি, এসব ফাঁকা কথায় অনর্থক সময় নষ্ট। মরার পর সবাই উড়ে পুড়ে ছাই হয়ে যায়, এই হ’ল মোক্ষ। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে ধর্ম প্রায় নেই বলতে গেলে। সেখানকার মানুষগুলো সবাই কি মৃত্যুর পরে নরকে যাচ্ছে? গরিবরা এখন যেন হয়েছে একটা খেলার বস্তু। সবাই তাদের ভালোবাসার জন্য মহা ব্যস্ত। আমাদের দেশে অনেক গরিব, বেশ তো, তাদের সাহায্য করতে চান তো খুব ভালো কথা, মানুষের মতন তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়ান, দয়া ক’রে তাদের মাথার ওপরে আর ধর্ম চাপাবেননা। যথেষ্ট হয়েছে। আমার মতে, ধর্ম হ’ল বড়োলোকদের আর পাগলদের সময় কাটাবার একটা জিনিস! গরিবরা কোনোদিন ধর্মচর্চা করেনা। তারা অন্ধের মতন শুধু কিছু-কিছু ধর্মীয় সংস্কার মেনে আসে, তাই তাদের খেলার পুতুল হিসেবে চালাতে অন্যদের সুবিধে হয়। এখন তাদের মন থেকে ধর্ম একেবারে মুছে দেওয়া দরকার।
আমার এই অহেতুক বাগাড়ম্বরের ফল মোটেও ভালো হ’লনা। শ্রোতাদের মধ্য থেকে প্রতিবাদ উঠল। ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ। সভাপতি মহাশয় আবার দশ মিনিট ধ’রে আমাকে উপদেশ দেবার ছলে শ্লেষের সঙ্গে যা-বললেন, তার একটাই অর্থ। আমি একটি নির্বোধ! আমার মন এখনও জড় অবস্থা কাটিয়ে ওঠেনি।
৮
কলকাতায় রাসবিহারী এভিনিউর ফুটপাতে দাঁড়িয়ে বিকেলবেলা একটি তরুণী একটি তিনতলা বাড়ির ওপরের জানলার দিকে মুখ করে ডাকছিল, কৌশিক কৌশিক। অবিলম্বে জানলা খুলে গেঞ্জি-পরা একটি স্বাস্থবান যুবক মুখ বাড়িয়ে বলল, কে, ঝুমা? ওপরে আয়। মেয়েটি বলল, ওপরে আর যাবনা, একটা শুধু দরকারি কথা আছে। যুবকটি নিচে নেমে এলো এবং শুধু একটিমাত্র দরকারি কথা নয়, অনেক দরকারি কথা হ’তে থাকে, পাশের সিগারেটের দোকান থেকে আমি যে দু-এক টুকরো শুনতে পাই, তাতে বুঝতে পারি এরা কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী। আমার রোমাঞ্চ হয়।
আমাদের ছাত্রজীবনে, খুব বেশিদিন আগের কথাও নয়, আমরা কলেজের সহপাঠিনীদের সঙ্গে খুব সহজে দেখা করতে পারতামনা, অনেক ছলছুতো খুঁজতে হ’ত। মেয়েদের বাড়িতে দেখা করতে যাওয়া প্রায় নিষিদ্ধই ছিল। গ্রীষ্মের ছুটির দীর্ঘ ব্যবধানে অতিষ্ঠ হয়ে একবার এক সহপাঠিনীর বাড়িতে দেখা করতে গিয়ে তার ব্যায়ামবীর দাদার কাছে আধ ঘণ্টা ইন্টারভিউ দিতে হয়েছিল এবং টেবিলের তলায় আমার পাদুটো কাঁপছিল ঠক্ঠক্ ক’রে। আর ছেলেদের বাড়িতে কোন অনাত্মীয় মেয়ের আগমন পাড়াপ্রতিবেশিদের উঁকিঝুকি দেওয়ার মতন!
একজন ক্রিকেট খেলোয়াড়কে যে-বয়সে বৃদ্ধ বলা হয়, সেই বয়েসটা একটা গীর্জার পক্ষে কিছুইনা। তেমনি পৃথিবীর বনেদি শহরগুলি, যেমন বাগদাদ, জেরুজালেম বা বারাণসী, এদের তুলনায় ২৯০ বছরের কলকাতা নিতান্তই নাবালক। কলকাতার কোন পূর্বস্মৃতি নেই, কোন ঐতিহ্য নেই। এই হিসেবে কলকাতার নাগরিকরা দায়মুক্ত, এখানকার নিয়মরীতি আপনা-আপনি তৈরি হয়ে উঠছে।
কলকাতা সবসময় জীবন্ত। হঠাৎ-হঠাৎ উত্তেজনার ঝড় ওঠে, কখন প্ৰচণ্ড হিংস্র হয়ে পড়ে, কিন্তু কলকাতা কখনই ঝিমিয়ে থাকেনা। দিল্লির ছাত্ররা যখন ব্রাহ্মণ-হরিজনে বিবাহ নিয়ে বিক্ষোভ জানায়, কলকাতার ছাত্ররা তখন বিশ্বরাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত। ভিয়েতনাম বা কিউবার ঘটনা নিয়ে যখন কলকাতার ছাত্ররা অস্থির, তখন বোম্বাই-মাদ্রাজ-দিল্লির ক্যামপাস শান্ত নিঃস্তরঙ্গ। একসময় কলকাতার ছাত্ররা সুরেন বাড়ুজ্যের ঘোড়ারগাড়ির ঘোড়া খুলে নিজেরা টেনে এনেছিল। বাংলার রাজনীতির সঙ্গে বাংলার ছাত্ররা বহুকাল জড়িত। অবশ্য রাজনীতি থাকলে দলাদলি থাকবেই। একসময় রাজপুতদের অসাধারণ শৌর্য-বীর্য থাকলেও বারো রাজপুতের তের হাড়ি হবার কারণে তারা পরাধীন হয়ে যায়। কলকাতার ছাত্ররাও রাজনৈতিক দলাদলিতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে—এবং দলাদলির ফলে মাঝে-মাঝে মারামারি। আমাদের ছাত্রবয়সে নিজেদের মধ্যে মারামারিটা ঘুষোঘুষি বা ইটেই টিতে থেমে থাকত—কিন্তু বোমা, পাইপগান নিয়ে কোন সহপাঠিকে একদম খন ক’রে ফেলার ব্যাপারটি কেউ দেখিনি। মাঝখানের কয়েক বছর এই নৃশংস হৃদয়-বিদারক ব্যাপারটি ঘটেছিল, সুখেরকথা ছাত্ররা এখন আর খুনী হতে চায় না। যতদিন ছাত্র থাকবে, ততদিন মারামারি থাকবেই, সে খেলার রেজাল্ট নিয়েই হোক বা রাজনীতি নিয়েই হোক্। কিন্তু সে-মারামারি ঘুষোঘুষিতেই নিবদ্ধ থাকলেই ভালো। কলকাতার ছাত্রদের পক্ষে সবচেয়ে প্রশংসনীয় কথা এই, এরা কোনদিনই ভাষা, প্রাদেশিকতা কিংবা সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্ন নিয়ে দ্বন্দ্বে মাতেনি। সেদিক থেকে এখনকার ছাত্রসমাজ অনেক মুক্ত, অনেক রুচিশীল।
কলকাতার যৌবন দুরন্ত কিন্তু অশালীন নয়। দিল্লিতে কোন কলেজের ছাত্র সাইকেলে চেপে যেতে-যেতে রাস্তার পাশে বাসের জন্য অপেক্ষমাণ কোন তরুণীর বেণী ধ’রে টান মারল আর মেয়েটি যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠল—এই বীভৎস দৃশ্য আমার নিজের চোখে দেখা। কলকাতার যুবসমাজ কোন পথযাত্রিণীর রূপযৌবন সম্পর্কে দু-চারটে মধুর উক্তি করে নিশ্চয়ই, কখন-কখন তাদের ভাষা কলেজ বাথরুমের দেওয়ালের ভাষার পর্যায়েও নেমে যায় বটে, কিন্তু কখনোই কোন অচেনা নারীর সম্ভ্রমহানি করেনা, শারীরিকভাবে আঘাত দেওয়া দূরে থাক্। তাছাড়াও কলকাতা ছাড়া এখনও ভারতের আর কোথাও ট্রামে-বাসে মহিলাদের দেখে পুরুষরা জায়গা ছেড়ে দাঁড়ায়না।
অনেক অতিকায় কলেজের মধ্যস্থল কলেজ স্ট্রিট হওয়ায় ছাত্রদের এটি একটি প্রধান কেন্দ্র। এই কলেজ স্ট্রিটে কতবার কতরকম ঝড় বয়ে গেছে। এখানকার কফি হাউস যুবসমাজের একটি প্রাণের জায়গা। দু-পাঁচ বছর পর-পর আড্ডাধারীরা বদলে যায়, কিন্তু আড্ডার স্রোত অব্যাহত থাকে। এখনও দেখতে পাই ঠিক আমাদের মতনই একদল অবিকল সেই একই ভঙ্গিতে তর্কে মেতে টেবিল ফাটাচ্ছে।
কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসে যে কেউ গিয়ে এককাপ কফি কিনে খেতে পারে তবু কেন যেন র’টে যায়, যারা কফি হাউসে যায় তারাই ইন্টেলেক্চুয়াল। কফি হাউসের অনেক টেবিলই আজ অনেক সহিত্য পত্রিকার অফিসিয়াল অফিস। আড্ডাধারীদের পকেট থেকে বেরোয় টাকার বদলে ভাঁজ-করা কবিতা। কলকাতা গোপনে-গোপনে কবিদেরই শহর।
বারোয়ারী পুজো ও খেলার মাঠে কলকাতার যৌবন বেশি স্পষ্টভাবে চোখে পড়ে। মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল ম্যাচের পর বিশাল এক যৌবনস্রোত ময়দান ছেয়ে ফেলে। বন্যার মতন ক্রমশ তা রেড রোড পেরিয়ে ধেয়ে আসে। কতরকমের জামা আর কতরকমের চুলের বাহার। বাসে ঝুলে প্রাণ বিপন্ন ক’রে হাসতে-হাসতে বাড়ি ফেরে। এইসব সময় যুবকদের কেউ সামান্য কোন উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহারের সমালোচনা যখন করেন তখন আমি আশ্চর্য হয়ে যাই। এ আর কী উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহার। এরচেয়ে কতগুণ উচ্ছৃঙ্খল তারা হতে পারত, হবার কথা ছিল। একলক্ষ যুবক একসঙ্গে হ’লে কী-না করতে পারে।
বারোয়ারি পুজোয় ছেলেরা একটু চাঁদার টাকায় ফুর্তি-টুর্তি করে। কীভাবে যেন রটে গেছে দুর্গাপুজো করে পাড়ার ভালো ছেলেরা আর কালীপুজো করে পাড়ার মস্তানরা। নিশ্চয় এটা সত্যি নয়—তবু এরকম একটা রটনা চলছে। যারাই যে-পুজো করুক-না কেন, কিন্তু খানিকটা আনন্দ-টানন্দ তো তারা করবেই। যে শহরে খেলার মাঠের সংখ্যা নগণ্য, ভালো বেড়াবার জায়গা নেই, বিশ্রী কতকগুলো সিনেমা ছাড়া সময় কাটাবার কোন ব্যবস্থা নেই সেখানে যুবকরা বছরে একবার—দুবার অন্তত আনন্দ করতে সুযোগ নেবেনা? তারা শান্ত শিষ্ট লক্ষ্মী ছেলে হয়ে থাকবে? যে-দেশের যুবসমাজ শান্তশিষ্ট লক্ষ্মী, সে দেশের সর্বনাশ হতে আর দেরি থাকেনা।
কলকাতার যৌবনের একটা ভারি করুণ দিক আছে। বিকেলবেলা নানান পথের মোড়ে-মোড়ে যুবকরা দাঁড়িয়ে জটলা করে—ঘণ্টার পর ঘণ্টা একই জায়গায়, পা বদলে নেয় মাঝে-মাঝে। এই দৃশ্য দেখে আমার কষ্ট হয়, বুক টনটন করে। এরা বেকার, এদের আর কোন যাবার জায়গা নেই। স্বাস্থ্যবান, সুসজ্জিত সব যুবা। চুপচাপ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে—এর চেয়ে অর্থহীন আর কী থাকতে পারে? এরা কাজ করতে অরাজী নয়, কিন্তু এদের কেউ কাজ দিতে পারেনা। শুধু চাকরী দেওয়াই নয়—একসঙ্গে কোন বড়ো কাজে নামার জন্য এদেরকে কেউ ডাকেনি। আমি মাঝে-মাঝে স্বপ্ন দেখি, একদিন কলকাতার দু-তিন লক্ষ যুবক একসঙ্গে শাবল গাঁইতি নিয়ে কোন একটা রাস্তা তৈরি করা বা বাঁধ বাঁধা কিংবা কোন খালকে গভীরভাবে নাব্য ক’রে দু-পাশে সুন্দর রাস্তা গ’ড়ে একটি সুদৃশ্য জিনিস কলকাতাকে উপহার দিয়েছে।
৯
হঠাৎ একদিন শ্যামপুকুর স্ট্রিট ধ’রে হাঁটতে-হাঁটতে, থমকে দাঁড়িয়ে ভেবেছিলুম, কোন টাইম মেশিন কি আমাকে তিরিশ-পঁয়তিরিশ বছর আগে ফিরিয়ে নিয়ে গেছে? এই সেই আমার কৈশোরের চেনা পথ, প্রত্যেক দিন এই পথে হেঁটেছি, প্রত্যেকটি বাড়ি অবিকল একরকম আছে, কোন-কোন বাড়ির রকের আড্ডা এতগুলি বছর ধ’রে একইরকম চলছে। রাস্তার মানুষদের মধ্যে যে-কোন মুহূর্তে একজন কেউ আমার ডাক-নাম ধ’রে ডেকে উঠবে। অদূরের একটি বাড়িতে আমার কৈশোরের প্রেমিকা বিকেলে গা ধুয়ে, ধপধপে সাদা ফ্রক পরে, মাথার চুলে লাল রিবন বেঁধে রাজহংসীর মতন গাড়ি-বারান্দায় এসে দাঁড়াবে!
উত্তর কলকাতার কোন-কোন রাস্তায় গেলে সত্যিই মনে হয়, সময় যেন থেমে আছে!
কলকাতা শহরের সঙ্গে আমার জন্ম-সম্পর্ক নেই, তবে অতি শৈশব থেকেই আমি এখানে লালিত-পালিত। আমার কৈশোর ও যৌবনের অনেকটা সময় কেটেছে এই শহরের উত্তর খণ্ডের বিভিন্ন রাস্তার নানানরকম ভাড়া-বাড়িতে।
তারপর চ’লে এসেছি দক্ষিণ কলকাতায়, তা-ও প্রায় দেড় যুগ হয়ে গেল। তবে, শহরের ঠিক দক্ষিণভূমিতে আমার অবস্থান নয়, বলা যায় আমি শূন্যবিহারী, আমার বর্তমান বাসস্থানের অবিকল বর্ণনা আছে হাসান রাজার একটি গানে: কী ঘর বানাইনু আমি শূন্যেরই মাঝার লোকে বলে, বলে রে, ঘর বাড়ি ভালো না আমার!
শহরের দুটো দিকই ভালো ক’রে দেখেছি ব’লে মনে হয়, এ যেন প্রকৃতপক্ষে আলাদা দুটো শহর। বুডা আর পেস্ট মিলে যেমন বুডাপেস্ট নগরী, সেইরকম গঙ্গার দু-তীরে হাওড়া ও কলকাতা মিলে একটি বৃহৎত্নগরী হতে পারত, কিন্তু তা হ’লনা, হাওড়া রয়ে গেল মফস্বলে, কলকাতারও উত্তর-দক্ষিণে ঠিক যেন জোড় মিললনা।
আমাদের ছেলেবেলায় গোটা দক্ষিণ কলকাতারই ডাক নাম ছিল বালিগঞ্জ। আশ্চর্য ব্যাপার এই যে বালি কিংবা গঞ্জ এই দুটি শব্দের কোন অনুষঙ্গই মনে আসতনা, বালিগঞ্জ শুনলেই মনে হ’ত যেন উদ্যানময়, অতিপরিচ্ছন্ন এক সুদৃশ্য এলাকা, যেখানকার ছেলেরা অত্যন্ত চালিয়াত হয়। (অনেক গল্প-উপন্যাসে চালিয়াত যুবকদের বর্ণনায় তাদের বালিগঞ্জের ছেলে বলা হ’ত, দূরপাল্লার ট্রেনযাত্রায় প্রবাসী বাঙালিদের সঙ্গে আলাপ হ’লে যখন কেউ জিজ্ঞেস করত, কলকাতায় কোথায় থাকেন, তখন নৈহাটি-কোন্নগরের ছেলেরাও অম্লান বদনে বলত, বালিগঞ্জ!) আর সেখানকার মেয়েরা ঠোটে লিপস্টিক মাখে ও কুকুর পোষে। এরকম রোমহর্ষক গুজবও শুনেছি, বালিগঞ্জের মেয়েরা নাকি ‘বুক-কাটা’ জামা পরে। এরকম একটা রসিকতাও চালু ছিল, ‘বালিগঞ্জের মেয়েরা খুব খোলা—মেলা হয়, তাই না?’ ‘কেন রে?’ ‘ওরা সব সাউথ ফেসিং কিনা!’
প্রায় টুরিস্টদের মতন সাইট সিয়িং-এর উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা মাঝে-মাঝে দোতলা বাসে চেপে বালিগঞ্জের লেক ও রাসবিহারী এভিনিউ দেখতে আসতুম। দু-পাশে বৃক্ষশোভিত এমন সুবিশাল সরণী, যার মাঝখান দিয়ে ঘাসের ওপরে স্টিমারের মতন ট্রাম চলে, এমন সুন্দর রাস্তা উত্তর কলকাতায় একটিও ছিলনা। আর-একটি অপূর্ব সুন্দর পথ ছিল ম্যাণ্ডেভিল গার্ডেন্স, যেখান দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে মনে হ’ত বিলেত-টিলেত বোধহয় এরকমই। (সেই সুন্দর পথটিকে একালের বহুতল আবাসন-নির্মাণকারীরা হত্যা করেছে!)
দক্ষিণ কলকাতার ছেলেরাও কি এরকম উত্তর-কলকাতা সন্দর্শনে যেত? আমি পরবর্তীকালে দক্ষিণ কলকাতার অনেক মানুষকে দেখেছি, যাদের কাছে বৌবাজার স্ট্রিটের ওপারের অংশটি প্রায় অজানা। দুর্গাপুজোর সময় অধিক রাত্রে এদিক থেকে অনেকে বাগবাজার কিংবা সিমলার ঠাকুর দেখতে যান বটে, কিন্তু হরি ঘোষ স্ট্রিট কোথায়, এ-কথা জিজ্ঞেস করলে আকাশ থেকে পড়বেন। ‘হরি ঘোষের গোয়াল’ বাংলা প্রবাদের মধ্যে ঢুকে গেছে, সেই হরি ঘোষের নামের বিখ্যাত রাস্তাটি এদিককার অনেকেই চেনেননা।
দেখবার জিনিস উত্তর কলকাতাতেও বহু আছে, দক্ষিণ কলকাতার চেয়ে বেশিই আছে। এক-একখানা বাড়িরই কী সৌষ্ঠব! ছেলেবেলায়, আমরা রাজা নবকৃষ্ণ দেবের বাড়িতে খেলতে যেতুম। এখনও রাজবাড়ি বললে ঐ-বাড়িটির কথাই প্রথমে আমার চোখে ভাসে, যদিও পৃথিবীর বহু দেশের অনেক বড়ো-বড়ো রয়াল প্যালেস আমি দেখেছি। রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রিটের একটা অংশের সবকটা বাড়িই যেন ছিল রাজালয়। ঐরকম একটি বাড়ির বারান্দায় এক ষোড়শীকে দেখে প্রথমে আমার শ্বেতমর্মর মূর্তি ব’লে ভ্রম হয়েছিল, তারপর সে একটা হাত তুলে চুলে রাখতেই আমার সর্বাঙ্গে শিহরণ হ’ল, সেই প্রথম আমার রাজকন্যা দর্শন। সেই কন্যার পায়ের নখেরও যোগ্য নয় বালিগঞ্জের কোন মেয়ে!
গ্রে স্ট্রিট ও কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের মোড়ের জায়গাটা আমার জীবনে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে, কারণ, ঐখানে, হাতিবাগান বাজারের সামনে, আমি ব্রিটিশ শাসনের প্রত্যক্ষ স্পর্শ পাই। আমি পরাধীন আমলের কিশোর, কিন্তু তখনও ততটা বড়ো হইনি যাতে স্বাধীনতা-সংগ্রামে অংশ নিতে পারি। আমার তখন এগারো বছর রয়েস, বাবার সঙ্গে বাজার করতে গেছি, কী একটা মিছিল এসে পড়ায় হঠাৎ খুব হুড়োহুড়ি প’ড়ে গেল, আমি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলুম বাবার কাছ থেকে ইট বর্ষণ ও লাঠি চালনার মধ্যে দিশেহারা হয়ে আমি বাড়ির দিকে পালাবার চেষ্টা করছি, এইসময় যমদূতের মতন এক লালমুখো সাহেব পুলিশ অফিসার ঠিক বেড়াল—ছানার মতন আমার কাঁধ ধ’রে শূন্যে তুলে ছুঁড়ে ফেলে দিল। পাগলের মতন ছিল তার ভাব-ভঙ্গি। সেদিন বাড়ি ফিরে আমি সুভাষ বোসের ছবির সামনে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে শপথ করেছিলুম, বড়ো হয়ে আমি অন্তত একটি ইংরেজ খুন করবই। তার বছর দু-একের মধ্যেই অবশ্য ইংরেজরা এ-দেশ ছেড়ে চ’লে যায়।
ঐ হাতিবাগান বাজারের প্রায় উল্টোদিকেই ছিল সারি-সারি পুতুল-দারোয়ান বসানো দত্তদের বাড়ি। শুধু ধনী নয়, ঐ-দত্তরা যে জ্ঞানে-গুণেও অনেক উঁচু, সে-কথাও জানা ছিল আমাদের। দার্শনিক হীরেন দত্ত, মঞ্চ-যুবরাজ অমর দত্ত, কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, এঁরা সব ঐ-বাড়ির মানুষ। ঐ-বাড়ির সাহিত্যিক আড্ডাও বিখ্যাত ছিল, সামনে দিয়ে যেতে-যেতে কতবার সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে-চেয়ে ভেবেছি, কোনদিন কি ঐ-বাড়িতে প্রবেশের অধিকার পাব?
পাথুরেঘাটার মল্লিকবাড়ি কিংবা চোরবাগানের সিংহীবাড়ি ছাড়াও ঐ-অঞ্চলে আরও কত যে মনোহর অট্টালিকা ছিল তখন। পুরো এলাকাটাই ছিল প্রাসাদপুরী। তখন মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীরা ঐসব বাড়ি দখল করার উদ্যমে মাতেনি, গত শতাব্দীর বনেদী বাঙালিয়ানার বেশ কিছু চিহ্ন ঐ-অঞ্চলে ঘোরাফেরা করলেই পাওয়া যেত। ঐরকম সব বাড়ি ও সাংস্কৃতিক আবহাওয়া দক্ষিণ কলকাতায় কোথায়? অবশ্য এদিকেও ভাওয়ালের রাজবাড়ি বা নাটোরের রাজাদের চিত্তাকর্ষক বাড়ি ছিল, কিন্তু সেগুলি পূর্ববঙ্গের জমিদারদের, পুরোনো কলকাতার কালচারের আমেজ সেখানে ঠিক পাওয়া যেতনা।
পাথুরেঘাটার মন্মথনাথ ঘোষের বাড়িতে দু-একবার গেছি গানের জলসা শুনতে। এই মন্মথনাথ ঘোষ ছিলেন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের বিরাট পৃষ্ঠপোষক। তাঁর উদ্যোগে গঠিত অল বেঙ্গল মিউজিক কনফারেন্সের খ্যাতি ছিল ভারতব্যাপী। মন্মথনাথ ঘোষের নিজের বাড়ির যে অন্তরঙ্গ জলসা, তা শোনার সুযোগ পাওয়া ছিল এক দুর্লভ অভিজ্ঞতা। সেই সময়কার ঠুংরী ও খেয়ালের শ্রেষ্ঠ শিল্পী ওস্তাদ বড়ে গুলাম আলী ঐরকম এক আসরে তাঁর পুত্র মুনাব্বরকে উপস্থিত করলেন শ্রোতাদের সামনে। বাবার দিকে পেছন ফিরে ব’সে মুনাব্বর যে চুক-চুক ক’রে মদ্যপান করছিল, সেই দৃশ্যটা আমার মনে গেঁথে আছে।
উত্তর কলকাতার কয়েকটি বনেদী বাড়িতে আমি প্রবেশ-অধিকার পেয়েছিলুম গৃহ-শিক্ষকতার সূত্রে। সেইরকম একটি বাড়ির নাম ছিল মিত্তিরবাড়ি। আমাদের পুরসভা যদি নগর-সৌন্দর্য রক্ষা সম্পর্কে সচেতন হ’ত, তাহ’লে ঐরকম বাড়িগুলিকে অটুট-অবিকৃত অবস্থায় রেখে দিত নিশ্চয়ই। পৃথিবীর বড়ো-বড়ো শহরে সেরকমই করা হয়। ঝামাপুকুরে এমন একটি বৃহৎ প্রাসাদ ছিল, যার বারমহল ও অন্দরমহলের মধ্যে যাতায়াতের জন্য রেল লাইন বসানো ছিল। সে—বাড়ির কথা আমি শুনেছি মাত্র, চোখে দেখিনি, তবে খবরের কাগজে যখন সেই বাড়িটি বিক্রি হয়ে টুকরো-টুকরো হয়ে যাবার কথা পড়েছিলুম, তখন দুঃখ হয়েছিল খুব
মিত্তির বাড়িটিও ছিল বিশাল। লোহার গেটের পাশে ঘণ্টা ঘর, একজন দ্বারবান প্রত্যেক ঘণ্টায় ঘণ্টা বাজাত তা শুনে পথচারীরা ঘড়ি মিলিয়ে নিত গেটের ওপাশে বিস্তীর্ণ বাগান, বাইরে থেকে দেখে মনে হ’ত যেন ঐ-বাগানের শেষ নেই। বাগানের মাঝে-মাঝে নগ্ন পুতুল-পরী ও ফোয়ারা। একটি মস্ত বড়ো মজলিশ-কক্ষে অন্তত তিরিশ বত্রিশটা নানান আকারের ঘড়ি, সেখানে এক বৃদ্ধ মিত্তিরমশাই একটি শ্বেতপাথরের টেবিলে ব’সে ঢুলতেন, তাঁর উল্টোদিকে বসা একজন মাইনে-করা লোক তোতা পাখির মতন গীতা পাঠ ক’রে যেত। এই সুররিয়ালিস্টিক দৃশ্যটি গত শতাব্দীর নয়, মাত্র এই সেদিন, পঞ্চাশের দশকের। বাঙালি বনেদিয়ানার এই দৃশ্য সম্ভবত চিরকালের মতন মুছে গেছে।
সে-বাড়িতে আমি দুটি ফুটফুটে ছেলে-মেয়েকে পড়াতুম। মেয়েটির মা বিশেষ প্রয়োজনে কোন-কোনদিন আমার সঙ্গে পর্দার আড়াল থেকে কথা বলতেন। তাঁকে আমি কোনদিন চক্ষে দেখিনি, দেখার কৌতূহল ছিল অদম্য। আমি তখন পাঁচরকম ভাড়াটেওয়ালা বাড়িতে থাকি, পর্দানশিন মহিলাদের কথা শুধু বইতেই পড়েছি। আরও আশ্চর্যের কথা এই যে, আমার সেই ছাত্রীটির মা বেশ কয়েক বছর বিলেতে কাটিয়ে এসেছিলেন। আমার ছাত্রীটিও বাবা-মায়ের সঙ্গে বছর দু-এক বিলেতে থেকে এসেছিল, কিন্তু আমার সঙ্গে কথা বলার সময় সে একটিও ইংরিজি শব্দ ব্যবহার করতনা। কলকাতাতেও সে মিশনরি স্কুলের ছাত্রী, তবু বাংলা গল্পের বই পড়ার আগ্রহ প্রচণ্ড। এখনকার বিলেত-আমেরিকা ঘুরে—আসা ফরফরিয়াদের দেখলে আমার সেই ছাত্রীটির কথা মনে পড়ে। এখনকার মিশনরি স্কুলে-পড়া বাঙালি ছেলেমেয়েদের বাংলা বলতে যেন কত কষ্ট!
অ্যারিস্টোক্র্যাসির যত দোষই থাক, আচার-ব্যবহারে একটা উন্নত রুচিবোধ, শিল্প-সংস্কৃতির প্রীতি ও পৃষ্ঠপোষকতা, যা তারা গ’ড়ে তুলেছিল, সেরকমটি আর পাওয়া যাবেনা। আমি অল্পবয়েস থেকেই জমিদারতন্ত্রকে ঘৃণা করি।
বনেদী বাড়ি যেমন দেখেছি, তেমন দেখেছি ঘিঞ্জি বাড়ি। উত্তর কলকাতার মতন অত সরু-সরু গলি আর এক বাড়িতে গাদাগাদি ক’রে অত মানুষের বাস, এরকম দক্ষিণ কলকাতায় নেই। উত্তর কলকাতার ভাড়াটেরা যেমন চেঁচিয়ে ঝগড়া করে, তেমনটি শোনা যায়না দক্ষিণে। ভাড়াটেবাড়ির একটি অতি পরিচিত লক্ষণ হ’ল, জল নিয়ে ঝগড়া। উত্তর কলকাতার যতগুলি বাড়িতে আমি থেকেছি, সব বাড়িতেই দেখেছি চৌবাচ্চা নামে বস্তুটি, যা দক্ষিণ কলকাতার কোন বাড়িতে দেখিনি। ঐ-চৌবাচ্চা তো শুধুমাত্র জলাধার নয়, রীতিমতন একটি প্রতিষ্ঠান, ঐ চৌবাচ্চাকে ঘিরে কতরকম কলহ, মান-অভিমান, এমনকি প্ৰেম! দক্ষিণ কলকাতায় যেটি বাথরুম, উত্তরের বাড়িগুলিতে তার নাম ছিল কলঘর। বাথরুম সংক্রান্ত প্রাকৃতিক ক্রিয়াকর্মগুলির নাম উত্তর কলকাতার লোকেরা অনায়াসে জোরে-জোরে উচ্চারণ করে, দক্ষিণে তা নতুন জেনারেশানের মুখে কদাচিৎ শোনা যায়। এদিকে বলা হয়, ছোট বাথরুম, বড় বাথরুম। জঙ্গলে পিকনিক করতে গিয়েও মেয়েরা ‘বাথরুমে’ যায়।
সাহেবদের বাড়িতে ছাদ থাকেনা, দক্ষিণ কলকাতার বাড়িগুলিতে ছাদ থাকলেও তার তেমন ব্যবহার নেই (ইদানীং অবশ্য টি. ভি. অ্যান্টেনা লাগাবার জন্য ছাদের সার্থকতা দেখা দিয়েছে)। উত্তর কলকাতায় ছাদ একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান। ঘেঁসাঘেঁসি বাড়ি বলে অনেকসময় এক ছাদ থেকে অন্য ছাদে লাফিয়েও চ’লে যাওয়া যায়। এ-বাড়ির মেয়েরা ছাদের পাঁচিলে হেলান দিয়ে ও—বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে গল্প করে! বাড়ির মধ্যে জায়গা কম ব’লে বিকেলের দিকে ছাদে এলে মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলা যায়। ছাদের জলের ট্যাঙ্কের আড়ালে ব’সে প্রথম সিগারেট টানতে শেখা। চিলেকোঠার মধ্যে সন্ধ্যার প্রায়ান্ধকারে প্রথম চুম্বনের অভিজ্ঞতা। বছর তিরিশেক আগেও বহু বাংলা প্রেমকাহিনীর পটভূমি ছিল বাড়ির ছাদ।
দক্ষিণ কলকাতায় বাড়ির বাচ্চারা যতটা ছাদ ব্যবহার করে, বড়োরা ততটা নয়। গ্রীষ্মকালে ছাদে ঘুমোবার চলন উত্তর কলকাতাতেই বেশি। মনে পড়ে, গরম ছাদের ওপর জল ছিটিয়ে, তার ওপর মাদুর কিংবা পাটি পেতে শোওয়া, এক—একদিন মাথার ওপর সরাসরি চাঁদ ও মেঘের খেলা দেখতে-দেখতে ঘুম আসেনা, আকাশের গভীরতা যেন স্তরে-স্তরে বেড়ে যেতে থাকে, মহাশূন্যের দিকে ছুটে যায় মনোরথ। এক-একদিন ঘুমের মধ্যে আচমকা ঝুপঝাপ বৃষ্টি, হুডুস ধাড়ুস ক’রে উঠে, মাদুর-বালিশ গুটিয়ে দৌড়। উত্তর কলকাতার ছাদে একটাও মশা ছিলনা, এটা স্পষ্ট মনে আছে যে কোনদিন মশারি টাঙাতে হয়নি, এখন কী অবস্থা কে জানে।
তথাকথিত বনেদিয়ানারও সমর্থক নই, কিন্তু ঐ মিত্তির বাড়ির মানুষদের ভদ্রতাবোধ ও সুষ্ঠু সহবত-জ্ঞানের মনে-মনে প্রশংসা না-ক’রে পারতুমনা।
উত্তর কলকাতায় ভাড়াটেবাড়িতে চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে ঝগড়াঝাঁটি হয় বটে, আবার প্রতিবেশীদের মধ্যে ভাবও বেশি। এক পাড়ার সবাই সবাইকে চেনে, বিপদে আপদে খবরাখবর নেয়, যে-কোন পরিবারের কেচ্ছা বা কর্তার চাকরির উন্নতির সংবাদ অন্য সবাই নিমেষে জেনে যায়। নিরাত্মীয় কোন লোক মারা গেলে পাড়ার ছেলেরা শ্মশানযাত্রায় কাঁধ দিতে আসে। দক্ষিণের জীবনযাত্রা সাহেবী ধাঁচের। একই ফ্ল্যাটবাড়ির দুজন মানুষ পরস্পরের নাম জানেনা। একই পাড়ার কোন যুবতীর আত্মহত্যার খবর পরের দিন খবরের কাগজে টের পাওয়া যায়।
শহরের দুদিকের ভাষারও স্পষ্ট প্রভেদ আছে। প্রধান তফাৎ তালব্য শ ও দন্তের স-এর ব্যবহারে। দক্ষিণে তালব্য শ বেশি, উত্তরে দন্তের স। এরা বলে বৃশটি, মিশটি, আর ওরা বলে ‘সাম্বাজারের সসীবাবু সাইকেল চড়ে সসরীরে সগ্যে যায়’। আরও তফাৎ আছে। দক্ষিণে বলা হ’ত, ‘আমার ওয়াইফ’ কিংবা ‘আমার গিন্নী, উত্তরে বলা হ’ত, ‘আমার উনি’ কিংবা ‘খোকার মা’। দন্ত্য ন-এর প্রতিও উত্তর কলকাতার পক্ষপাতিত্ব, নুচি, নঙ্কা, নেবু এসব ওদিকেই বেশি শোনা যায়। উত্তরে আমি একটি বিচিত্র ক্রিয়াপদের ব্যবহারও শুনেছি। একসময় আমরা একটি স্বর্ণকারের বাড়ির প্রতিবেশী ছিলুম। সে-বাড়ির একটি কিশোরী মেয়ের কণ্ঠস্বর ঠিক স্বর্ণমণ্ডিত ছিলনা, বরং কাংস্যবিনিন্দিতই বলা যায়, সে প্রায়ই তাদের সদর দরজায় দাঁড়িয়ে ছোটভাইকে ডাকত, ‘পটি, পাইলে আয়, হাইরে যাবি!’ সে-বাড়ির বয়স্করাও ঐ-ভাষাতেই কথা বলত। বাংলা সাহিত্যের চলতি ভাষার প্রয়োগে আমি কখনও পাইলে, হাইরের ব্যবহার দেখিনি। ঐ-পাড়াতেই আমি ছেলেদের ডাকনাম শুনতুম, পটল, ঝিঙে, আলু, বেগুন!
পুরসভার চোখে দক্ষিণ কলকাতা যেন দ্বিতীয় পক্ষের তরুণী ভার্যা। সেই দিকে নেকনজর বেশি। আমি দু-তরফেই বেশ-কিছু বছর কাটিয়েছি ব’লে পক্ষপাতিত্বটা বুঝতে পারি। তুলনামূলকভাবে দক্ষিণের রাস্তাগুলি বেশি পরিচ্ছন্ন। সাদার্ন এভিনিউয়ের মাঝখানটা দেখতে-দেখতে কেমন সুন্দর কানন-শোভিত হ’ল, উত্তরের কোন রাজপথের এমন রূপ বদল হয়নি। বালিগঞ্জ লেকে লিলিপুল আছে, সাফারি পার্ক হয়েছে, রোয়িং ক্লাব ও সুইমিং ক্লাব অনেকগুলি, সেই তুলনায় উত্তরের দেশবন্ধু পার্ক বা হেদো খুবই অনাদৃত। টালির নালার তবু যেটুকু সংস্কার হয়েছে, সেই তুলনায় বাগবাজারে খালের কিছুই হয়নি। দক্ষিণে এত আকাশ-ঝাড়ু বাড়ি উঠছে, উত্তরে কেন তেমন হ’তে পারেনা?
উত্তর কলকাতার অনেক রাস্তাতে গেলেই আমার সময় থেমে থাকার অনুভূতি হয়। কিছুই বদলায়নি, একটি বাড়ি ভেঙেও নতুন বাড়ি ওঠেনি, গলিগুলো সেইরকমই সরীসৃপের মতন, মনোহারি দোকানের কাচের বৈয়মগুলো যেন একটাও কমেনি বা বাড়েনি। এর যে-কোন একটি বাড়ির সদর দরজা ঠেলে যেন আমি অনায়াসে ঢুকে পড়তে পারি, ইস্কুলের বইয়ের বোঝা ছুঁড়ে ফেলে ব’লে উঠতে পারি, মা, খিদে পেয়েছে, জল-খাবার দাও!
১০
পণ্ডিতিয়ার মোড়ে আমরা চার-পাঁচজন দাঁড়িয়ে গল্প করছিলাম। আকাশ মেঘলা, যে-কোন সময় বৃষ্টি আসবে এইরকম একটা ভাব নিয়ে গত দু-তিনদিন খুব গুমোট গরম চলছে। আমাদের প্রত্যেকেরই মুখ ঘামে তেলতেলে। কথা বলতে-বলতে আমিই প্রথম দেখতে পেলাম ঝর্ণাকে। ত্রিকোণ পার্কের পাশ দিয়ে এসে সে এইমাত্র রাস্তা পেরুচ্ছে। ফলসা রঙের শাড়ি পরা, হাতে একটা হলুদ শপিং ব্যাগ।
এখন বিকেল সাড়ে পাঁচটা, এইসময় রাস্তার ট্রাম-বাস, মানুষের ভিড় একেবারে চূড়ান্ত হয়। এই মোড়ে কোন ট্রাফিক পুলিশ নেই, কিন্তু ঝর্ণা রাস্তা পেরুবার সময় সবকিছু যেন আপনা-আপনি থেমে গেল। চারদিকের রাস্তায় চারখানা দোতলা বাস, বিপরীতমুখী দুটি ট্রাম, এমনকি কোন দুরন্ত ট্যাক্সিও অন্যদের পাশ কাটিয়ে এগোবার চেষ্টা করলনা, সবাই যেন বলছে, এখন ঝর্ণা যাচ্ছে, ওকে পথ ক’রে দাও। এ যেন মোজেজের জন্য সমুদ্রের দু-ভাগ হয়ে যাওয়া।
অন্যরা কথা বলছে, ঝর্ণাকে দেখতে পায়নি, আমি চুপ ক’রে আছি। ঝর্ণা কি আমাদের কাছে আসবে? মেয়েরা অনেকসময় পুরুষদের সঙ্গে যেচে কথা বলতে আসেনা। আমি ঝর্ণার চোখ চোখে ফেলার চেষ্টা করলাম, যাতেও চিনতে পেরে একটু অন্তত হাসে। একটা গুমোট বিকেলে একটু হাসিই যথেষ্ট।
আমাকে দেখতে না-পেলেও ঝর্ণা এইদিকেই আসছে। ঈষৎ অন্যমনস্ক। মাটির দিকে চেয়ে হাতের ব্যাগটা দোলাচ্ছে। ঝর্ণার সঙ্গে আমার ততটা পরিচয় নেই, যাতে ওকে ডাকতে পারি। অবশ্য এতজন বন্ধুর মাঝখানে ওকে ডেকেই—বা কী হবে? যদি একলা কখন দেখা হয়, কোন-একটা বাগানের ধারে, আমি ওর সঙ্গে এলেবেলে কথার ছলে ওকে দু-চোখ ভরে দেখব! ঝর্ণার মুখের মধ্যে কিছু-একটা আছে, ঐ-মুখের দিকে তাকালেই মনটা আনন্দে ভ’রে যায়। শুধু চোখে দেখার এমন আনন্দ পৃথিবীর আর কোন মেয়ের কাছ থেকে বোধহয় পাওয়া যাবেনা।
ঝর্ণা হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। আমাকে নয়, সে সুদীপকে দেখতে পেয়েছে। অন্যদেরও সে চেনে। ঝর্ণা কাছে এগিয়ে আসতেই সবাই কথা থামিয়ে দিল। ঝর্ণার উপস্থিতির সন্মানে সবাই মাথা নীচু করল।
সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিকভাবে ঝর্ণা জিজ্ঞেস করল, এই, তোমরা কেউ ব্যালে দেখতে যাচ্ছনা? কয়েক মুহূর্ত কেউ উত্তর দিলনা।
সারা শহরে সোভিয়েত ব্যালে নিয়ে দারুণ মাতামাতি চলছে। বিশ্ববিখ্যাত বলশয় ব্যালে দল এসেছে, তাই নিয়ে কলকাতার মানুষ একেবারে উত্তাল। টিকিট নিয়ে কাড়াকাড়ি। রবীন্দ্র-সদনের সামনে, ময়দানে ভোর থেকে লাইন। দু-দিন আগে ঘোষণা করা হয়েছে সব টিকিট শেষ!
সুদীপ বলল, আমরা কেউ টিকিট পাইনি। ঝর্ণা বলল, আমিও পাইনি। একজন দুটো টিকিট দেবে বলেছিল, তারপর তার পাত্তা নেই। আমি দেখবনা?
ঝর্ণার মুখে একটুও ঘাম নেই, তার চটি-পরা পায়ে একটুও ধুলো নেই, তার গায়ের রং ঝর্ণার জলেরই মতন স্বচ্ছ।
আমার মনে হ’ল, এই শহরে যদি একজনেরও এ নৃত্য উৎসব দেখার যোগ্যতা থাকে, তবে তা ঝর্ণারই। সে কেন টিকিট পাবেনা? কর্তাব্যক্তিদের কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই! আমাদের সবার মুখে একবার ক’রে তাকিয়ে ঝর্ণা অভিমানের সঙ্গে বলল, আমার এত ইচ্ছে ছিল…
ঝর্ণা চ’লে যাবার জন্য পা বাড়াতেই সুদীপ বলল, এই ঝর্ণা, শোনো—
ঝর্ণা তবু দাঁড়ালনা, সে মানুষজনের মধ্যে মিলিয়ে গেল।
আমি তৎক্ষণাৎ দারুণ একটু চাঞ্চল্য বোধ করলুম। ঝর্ণা আমাদের প্রত্যেকের ওপর একটা দায়িত্ব দিয়ে গেছে। ঝর্ণার জন্য একটা টিকিট জোগাড় করা যাবেনা। এ কখনও হ’তে পারে?
আমি ঝর্ণার সঙ্গে কখনও সিনেমা-থিয়েটার দেখতে যাইনি। পাশাপাশি রাস্তা দিয়ে হাঁটিনি। কিন্তু এবারে দুটি ব্যালের টিকিট নিয়ে গিয়ে ঝর্ণাকে অনায়াসে বলতে পারি, তুমি আমার সঙ্গে যাবে? ট্রাম-বাস নয়, পণ্ডিতিয়ার মোড় থেকে ট্যাক্সিতে নিয়ে যাব ঝর্ণাকে। রবীন্দ্র-সদনের সিঁড়ি দিয়ে সে আমার হাত আলতো ক’রে ধ’রে উঠবে। তৃতীয় কিংবা চতুর্থ সারির ঠিক মাঝখানে বসব আমরা, নর্তকীরাও আমাদের দেখতে পাবে।
অন্তত তিরিশজনের কাছে টিকিটের জন্য দৌড়োদৌড়ি করলুম আমি। কয়েকজন পাত্তাই দিলনা। কয়েকজন বলল, আগে এলেনা কেন? কেউ-কেউ ক্ষীণ আশা দিয়ে বলল, কাল সকালে দেখা ক’রো। সকালে গেলে তারা বলে বিকেলে আসতে। কিংবা আবার পরের দিন দুপুরে।
শেষ পর্যন্ত একজন আমাকে নাছোড়বান্দা দেখে কৃপা করে, প্রায় শেষ মুহূর্তে একখানা মাত্র টিকিট দিল। তাও খুব কম দামের। ওপরতলার এত পেছনে বসতে হবে যে সেখান থেকে ভালো ক’রে দেখাই যাবেনা। তবু টিকিটটা পেয়েই আমি ছুটে গেলুম ঝর্ণাদের বাড়ি। ঝর্ণা অন্তত জানবে যে আমি তার জন্য চেষ্টা করেছি। আমি তার সঙ্গে যেতে পারবনা, সে একলাই যাক।
ঝর্ণাদের বাড়ির গলির মুখটায় পৌঁছতে-পৌঁছতেই দেখলুম, একটা গাড়ি বেরিয়ে যাচ্ছে, তাতে ঝর্ণা আর সুদীপ। ব্যালে দেখতেই যাচ্ছে নিশ্চয়ই। সুদীপের বাবার অনেক চেনাশুনো আছে ওপরমহলে। সুদীপ শুধু টিকিটটি জোগাড় করেনি, গাড়িও জোগাড় ক’রে ফেলেছে। সাদা সিল্কের শাড়িতে রাজহংসীর মতন দেখাচ্ছে ঝর্ণাকে। আমাকে ওরা কেউ দেখতে পেলনা।
এখন এই টিকিটটা নিয়ে আমি কী করি? এই টিকিট নিয়ে আমি ব্যালে দেখতে যাব? অসম্ভব! আমি এত স্বার্থপর হতে পারিনা। হলের মধ্যে ঝর্ণা হঠাৎ আমাকে দেখতে পেয়ে গেলে নিশ্চয়ই ভাববে, আমি তার জন্য টিকিট জোগাড়ের চেষ্টা করিনি, নিজের জন্য করেছি। এত কষ্টে সংগ্রহ-করা টিকিটটা আমি ছিঁড়ে ফেললুম।
ঝর্ণা যে শেষ পর্যন্ত দেখতে যেতে পেরেছে, তাতেই তো আমার খুশি হওয়া উচিত। সুদীপের ওপর আমি কৃতজ্ঞ।
কিন্তু পুরীর টিকিট?
কয়েকদিন পরই ঝর্ণার দাদা অনীশের সঙ্গে দেখা। কথায় কথায় বলল, নীলু, ট্রেনের টিকিটের ব্যাপারে তোর কেউ চেনাশুনো আছে? আমার মায়ের শরীরটা ভালো নেই জানিস তো, মাকে নিয়ে ঝর্ণা পুরী যেতে চাইছে, কিন্তু এক মাসের মধ্যে কোন রিজার্ভেশন পাওয়া যাচ্ছেনা।
আমি লাফিয়ে উঠে বললুম, হ্যাঁ, আমি জোগাড় ক’রে দেব!
কী ক’রে যে বললুম কে জানে! রেলের কোন লোককে তো আমি চিনিনা। বুকিং অফিসের সামনে বরাবর লম্বা লাইন দেখে এসেছি। তবে, এটাও জানি, সব সীট ভর্তি হয়ে যাবার পরেও কেউ-কেউ টিকিট পায়। ভি. আই. পি. কোটা নামে একটা নাকি ব্যাপার আছে। ঝর্ণার চেয়ে বড়ো ভি. আই. পি. আর কে আছে? ঝর্ণা তার মাকে নিয়ে পুরী যেতে চেয়েছে, তাকে যেতেই হবে!
অনীশ বলল, ওদের দরকার তিনখানা বার্থ রিজার্ভেশন। যদি চারখানা পাওয়া যায়? তাহ’লে আমিও যেতে পারি ওদের সঙ্গে। চলন্ত ট্রেনে ঝর্ণা আমার মুখোমুখি বসবে। ট্রেনের শব্দ ছাপিয়ে শোনা যাবে তার হাসির শব্দ। বাঙ্কে উঠে ঘুমোবে ঝর্ণা। আমি দেখব তার ঘুমন্ত মুখ। ঝর্ণা সমুদ্রে স্নান করতে নামবে, আমি জানি সমুদ্রের ঢেউ খেলা করবে তাকে নিয়ে, আকাশ ঝুঁকে আসবে তার জন্য। ট্রেনের টিকিট কে দেয়! বুকিং অফিসে গিয়ে শুনলুম, কোন আশা নেই। তবু যেতেই হবে। ঝর্ণাদের সঙ্গে আমাকে যেতেই হবে! বিশ্বদেবদার সঙ্গে অনেক ফুটবল খেলোয়াড়ের চেনাশুনো। খেলোয়াড়রা কি ইচ্ছেমতন টিকিট পায়? বিশ্বদেবদা আমাকে একটা চাকরি জোগাড় ক’রে দেবার আশ্বাস দিয়েছিলেন। বিশ্বদেবদাকে গিয়ে বলব, আমাকে চাকরি দিতে হবেনা। তুমি শুধু আমাকে পুরীর চারখানা টিকিট দাও?
বাস স্টপে একদিন ঝর্ণাকে দেখতে পেলুম দূর থেকে। একজন সখীর সঙ্গে গল্প করছে। হেসে-হেসে। আমি চট ক’রে স’রে গেলুম অন্যদিকে। পুরীর টিকিট জোগাড় না-ক’রে ঝর্ণার চোখের সামনে দাঁড়াবার যোগ্যতা আমার নেই। বালিগঞ্জ স্টেশনের কাছে একজন নাম-করা সাধুমহারাজ এসেছেন। ওঁর নাকি অনেকরকম অলৌকিক ক্ষমতা আছে। উনি তৈরি ক’রে দিতে পারেননা চারখানা ট্রেনের টিকিট? ওঃ, সে-বাড়ির সামনে গাড়িওয়ালা লোকদের ভিড়, আমাকে উনি পাত্তা দেবেন কেন? ভবানীপুরে এক বাড়িতে টিউশনি করেছিলুম কিছুদিন। যে—ভদ্রলোকের ছেলেকে পড়াতুম, তার কাপড়ের ব্যবসা। ছেলেকে তিনি হস্টেলে ভর্তি ক’রে দিয়েছেন। মাস্টার হিসেবে আমাকে তিনি অপছন্দ করতেননা, ছেলেটির মা মারা গেল বলেই তাকে হস্টেলে পাঠানো হ’ল। সেই ভদ্রলোক কি পারেন টিকিটের ব্যবস্থা ক’রে দিতে?
শেষ পর্যন্ত মনে পড়ল, সুদীপের কাছেই তো যাওয়া যেতে পারে। সুদীপ দুর্লভ রাশিয়ান ব্যালের একটি টিকিট এনে দিতে পারে আর চারখানা ট্রেনের টিকিট দিতে পারবেনা? সুদীপের বাড়িতে যেতেই ওর সঙ্গে দেখা হ’ল। আমাকে কিছু জিজ্ঞেসও করতে হ’ল না, সুদীপ নিজেই জানাল যে পরশু সে পুরী যাচ্ছে অফিসের কাজে। ঝর্ণারাও পুরী যেতে চায় শুনে সে ট্রাভেল এজেন্টের কাছ থেকে ওদের জন্যও টিকিট কিনে দিয়েছে। মোট চারখানা টিকিট। অতি সহজ ব্যাপার। এবারেও তো সুদীপের ওপর আমার কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। ঝর্ণা তার মাকে নিয়ে পুরী যেতে চেয়েছিল, যেতে পারাটাই তো বড়ো কথা। আমার বদলে চলন্ত ট্রেনের জানলায় ঝর্ণার মুখোমুখি বসবে সুদীপ। সমুদ্রে সুদীপই ওর পাশে থাকবে। ঝর্ণা জানতেও পারবে না, ওদের টিকিট জোগাড়ের জন্য আমি কত চেষ্টা করেছি। আমি পারিনি, কিন্তু আমার বাসনার তীব্রতায় কোন খাদ ছিলনা।
আমি ব্যাপারটাকে খুব শান্তভাবে গ্রহণ করবার চেষ্টা করলুম। সুদীপ ভালো ছেলে, সে ঝর্ণা ও তার মাকে যত্ন করবে। সুদীপের দায়িত্বজ্ঞান আছে। ওরা তো আবার ফিরে আসবেই, তখন আবার ঝর্ণার সঙ্গে দেখা হবে।
তবু রাত আটটায় আমি ঝর্ণাদের বাড়ির কাছের মোড়টায় না-গিয়ে পারলুমনা। একবার, এক ঝলক ঝর্ণাকে দেখতে চাই। আর-কিছু না, শুধু চোখের দেখা। ঐ-মুখখানি দেখলেই মন ভালো হয়ে যায়।
ডানদিকের ফুটপাথে আমি কেন দাঁড়িয়েছিলুম! ঝর্ণা বসেছে ট্যাক্সির বাঁদিকের জানলায়। চোখাচোখি হওয়া তো দূরের কথা, ঝর্ণাকে আমি দেখতেই পেলুমনা ভালো ক’রে। ট্যাক্সিটা হুস ক’রে বেরিয়ে গেল।
সঙ্গে-সঙ্গে আমার মনে হ’ল, ঝর্ণা আর কোনদিনই আমার হবে না। কখনও থিয়েটার বা নাচ দেখতে যাওয়া হবেনা তার সঙ্গে, এক ট্রেনের কম্পার্টমেন্টে ব’সে আমরা কোনদিন বেড়াতে যাবনা। সমুদ্র স্নান সেরে ঝর্ণা উঠে আসবে, সেখানে আমি থাকবনা। বুকটা এমন মুচড়ে উঠল যেন আমি অজ্ঞান হয়ে যাব। পরক্ষণেই নিজেকে বোঝালুম, আরে, এতটা আঘাত পাবার কী আছে? যারা বাসের টিকিট, ট্রেনের টিকিট, লটারির টিকিট অতি সহজে পেয়ে যায়, তারাই তো নারীদের নিয়ে যায়। সুদীপই ঝর্ণার যোগ্য, আমি তো একটা এলেবেলে। আমার আবার এত দুঃখের বিলাসিতা কিসের?
তবু আমি আপন মনে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে লাগলুম। কোথায় যাচ্ছি তার ঠিক নেই। একসময় খেয়াল হ’ল, হাওড়া ব্রিজের কাছে পৌঁছে গেছি। আরে যাঃ, এখন হাওড়া স্টেশনে যাওয়া যায় নাকি? তাছাড়া এতক্ষণে বোধহয় ঝর্ণাদের পুরীর ট্রেন ছেড়ে গেছে।
আবার পেছন ফিরলুম। রাস্তাগুলো ক্রমশ ফাঁকা আর অন্ধকার হয়ে আসছে। এখন সব রাস্তাই অচেনা। কলকাতার এসব অঞ্চলে আগে কখনও আসিনি মনে হয়। বড়ো-বড়ো বাড়ি, মাঝখান দিয়ে গাছপালা ঢাকা সরু-সরু পথ। কোন-কোন বাড়ির ওপরের দিকের জানলায় আলো।
ক্রমশ পৃথিবীটা খুব নিজস্ব হয়ে এল। এখন আর কেউ নেই।
কিছুটা পরিশ্রান্ত হয়ে আমি একটি রেলিং ধ’রে দাঁড়ালুম। কত রাত এখন কে জানে। চমৎকার জ্যোৎস্না উঠছে। রেলিংয়ের ওপাশেই একটা বেশ বড়ো বাগান। অনেকরকম ফুল, কিন্তু রাত্রিবেলা কোন ফুলেরই রং বোঝা যায়না! বাতাসে ফুলগুলি দুলছে, আমার নাকে এসে লাগছে সুগন্ধের ঝাপটা।
এত সুন্দর বাগান, এটা কার?
সেই বাগানের সৌন্দর্য যেন ঝর্ণার মুখের মতন, চেয়ে থাকতে যেন চোখ ফেরানো যায়না। এই বাগানটা কোনদিন আমার হবেনা, আমি এইবাগানে ঢুকবনা, এর ফুল ছিঁড়বনা। তবু এই বাগানটা আমার বুক ভরিয়ে দিচ্ছে। ফুলগুলো খেলা করছে, ডাকাডাকি করছে পরস্পরকে। কখন যেন ঢেউয়ের ঝাপটায় লাফিয়ে উঠছে। শোনা যাচ্ছে জ্যোৎস্নার হাসির শব্দ।
এমন জ্যোৎস্নার একটা বাগান আমি কোনদিন নিজের ক’রে পাবনা। সে—প্রশ্নই ওঠেনা। কিন্তু এখানে আমি অনেকক্ষণ চুপ ক’রে দাঁড়িয়ে থাকতে পারি। একটা চরম উপভোগে আমার শরীর যেন আবিষ্ট হয়ে আসছে। আমার আলিঙ্গনের মধ্যে ধরা দিয়েছে রূপ, আমার ওষ্ঠে চুম্বন করছে বাতাসের লাবণ্য। সুদীপ এ—কথা কোনদিন জানতে পারবেনা!