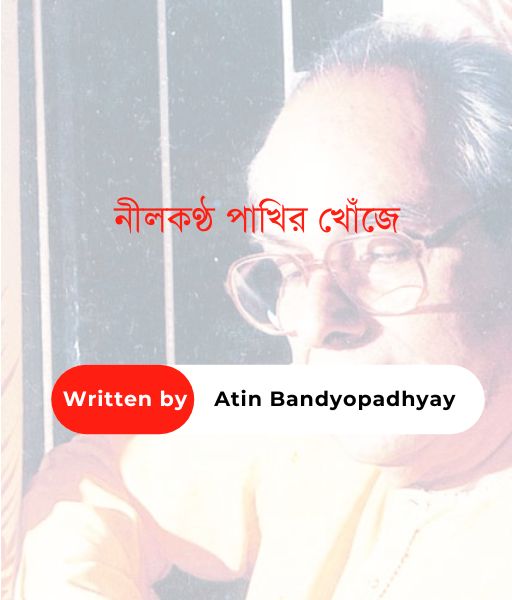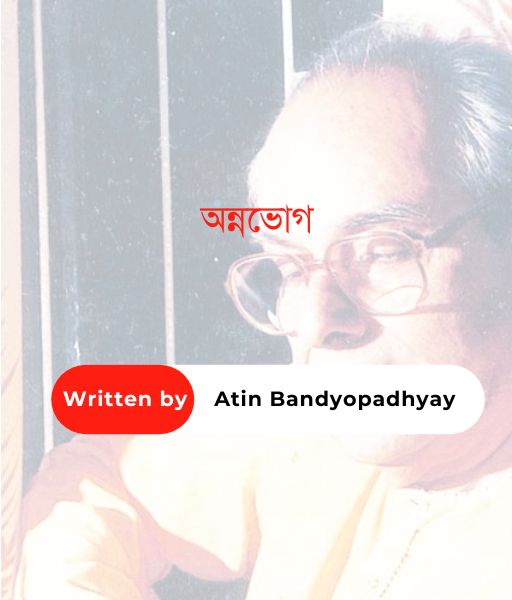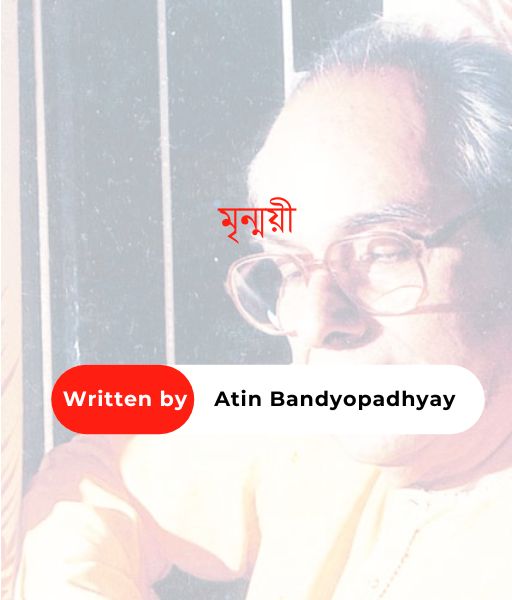নারী এবং নদীর পাড়ে বাড়ি – চার
তারপর অরণির এইভাবেই দিন যায়, বছর যায়।
একদিন সে স্কুল থেকে ফিরে না বলে পারেনি, এই তিথি শোন।
তিথি তার ঘরে জল তুলে দিয়ে গেছে। তারপর সে ছুটছিল বাড়ির অন্দরের দিকে। কাছারিবাড়ির পরে মাঠ, ঘাসের লন এবং দুটো জবাফুলের গাছ পার হয়ে পাঁচিলের দরজায় হয়তো ঢুকে যেত। তার জলখাবার, এই যেমন কখনও তেলমাখা মুড়ি, অথবা চিড়ে ভাজা, সঙ্গে বাদাম ভাজা কিংবা নাড়ু, কখনও ফুলুরি অথবা ফুলকপির সিঙারা, যা তাকে দেয়, সে নিয়ে আসে।
তিথি জবাফুল গাছের নীচে দাঁড়িয়ে বলল, ডাকছ কেন?
শুনে যা।
আমার এখন শোনার সময় নেই।
আছে। শুনে যা বলছি।
অরুদা। কোনও কারণে রেগে যেতে পারে, সে ইতস্তত করছিল, গাছের নীচ থেকে নড়ছিল না।
শুনে যা বলছি।
কী যে করো না। কী হয়েছে? কখন সেই সকালে দুটো মুখে দিয়ে গেছ, না খেলে পিত্তি পড়বে না। আমি আসছি।
না, আসছি না। আগে আয়।
অরু স্কুলের জামাও ছাড়েনি। এত নজর মেয়েটার। কখন সে ফিরবে, সেই আশায় হয়তো নদীর পাড়ে কিংবা সুপারিবাগানে হেঁটে বেড়ায়। না হলে, সে ফিরেই দেখতে পাবে কেন, এক বালতি জল আর কাঁসার ঘটিটি সিঁড়িতে রাখা আছে। না হলে ফিরেই দেখবে কেন, তার জামাপ্যান্ট ভাঁজ করা, চকির এক কোনায় সাজিয়ে রাখা, চাঁপা ফুল তুলেও একটা কাচের গেলাসে জলে ডুবিয়ে রাখে। এই ঘরের সব সৌন্দর্য তৈরি হয় তার হাতে। সে যা কিছু এখানে সেখানে ফেলে রাখে, তিথির কাজ তা গুছিয়ে রাখা।
এ জন্য অরুর নিজের উপরও রাগ হয়।
কিন্তু মুশকিল, কমলদা কিংবা বিশুদা ডাকলে তার ছুটে যাবার অভ্যাস—শীতে ব্যাডমিন্টন, বর্ষায় স্কুলের মাঠে ফুটবল, কিংবা স্কুলের প্রতিষ্ঠা দিবসে নাটক, এ—ছাড়া কত যে আকর্ষণ, মেজদা ঢাকা থেকে এলে তার সঙ্গে শিকারে যাওয়া, অথবা নদীর চরে ডাল ফেলে রাখা হয়, জোয়ারের জলে ডুবে যায় ডালপালা, ভাটার মুখে জল নামার আগে সব ডালপালা ঘিরে ফেলা হয় বাঁশের বানা দিয়ে। জল নেমে গেলে, সেই ডালপালা সরিয়ে দিলে জলে কাদায় তাজা মাছের ছড়াছড়ি। গলদা চিংড়ি, কালিবাউশ, ভেটকি থেকে কই পুঁটি ট্যাংরা কিছুই বাদ থাকে না। দাদারা পছন্দমতো মাছ ঝুড়িতে তুলে দিতে বলে, জেলেরা মাছের ঝুড়ি বাড়ি পৌঁছে দেয়, সে আর তিথি তার পেছনে পেছনে ছোটে।
তখন তার মনেই থাকে না, সে তিথির জন্য কাজ বাড়িয়ে রেখে যাচ্ছে। বই খাতা সব চকিতে ছড়ানো ছিটানো। কলম পেনসিল, জিওমেট্রি বক্স যেখানে সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকে। স্কুল থেকে ছুটে আসে। যেন সে তাড়াতাড়ি বের হতে না পারলে তার মজা উপভোগ করার সময় পার হয়ে যাবে। তিথি আছে, সে—ই সব করবে।
সে—ই সব তুলে রাখে। সাজিয়ে রাখে। জিওমেট্রি বক্স খোলা, বাক্সের সবকিছু এলোমেলো, তিথির কাজই হল, ঠিকঠাক তুলে রেখে দেওয়া। এত যে মজা উপভোগ করতে পারে তিথি আছে বলেই।
তিথি কেমন ভীরু পায়ে লন পার হয়ে এগিয়ে আসছে।
সে বুঝতে পারছে না তার কী দোষ।
অরু সিঁড়ি থেকে নড়ছে না।
তিথি অত্যন্ত ভীরু মুখেই বলল, আমি কী করেছি?
আগে কাছে আয়।
তিথি ভয়ে কাছে যাচ্ছে না।
বলোই না। আমি তো কাছেই আছি।
ঘরে আয়।
না ঘরে ঢুকব না।
ঢুকবি না?
তুমি কি আমাকে মারবে?
তোকে মারতে পারলে ভালো হত। তুই কখন রাতে বাড়ি যাস? সারাদিন বাবুদের বাড়িতে পড়ে থাকতে ভালো লাগে?
তিথি মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে।
রাতে তুই রোয়াকে বসে থাকিস কেন? তুই কি রাতে বাবুদের বাড়িতে খাস। তোকে কি তারা দু—বেলা খেতে দেয়।
দেবে না কেন? যখন যা বেশি হয় দেয়। সবাই খেলে কিছু তো পড়ে থাকেই। আমি আলাদা থালায় তুলে রাখি। ওতেই পেট ভরে যায়।
সারাদিন ধরে বাবুদের বাড়ির সবার উচ্ছিষ্ট খাবার খেয়ে বেড়াস? তোর খারাপ লাগে না।
বারে, খারাপ লাগার কী আছে। তুমি কি এজন্য আমাকে ডেকেছ? আমার কত কাজ জানো? তুমি জানো, ছোড়দির আজ পুতুলের বিয়ে। আমি না গেলে সব কাজ পড়ে থাকবে। পুতুলের জামাকাপড় আমি না গেলে পরাবে কে! দেরি হলে রাগ করবে। আমাকে খামচে দেবে। আমার ফ্রকও ছিঁড়ে ফেলতে পারে। ছোড়দির বেজায় রাগ জানো? আমাকে কি বলেছে জানো?
কী বলেছে!
তুমি নাকি ছোড়দিকে দেখলে পালাও।
মিছে কথা।
ছোড়দি মিছে কথা বলে না। ছোড়দি তো কাউকে ভয় পায় না। মিছে কথা বলতে যাবে কেন?
পালাই! বেশ করেছি। বলবি বেশ করেছি।
ছোড়দির সঙ্গে কথা বলো না কেন? তাই তো খেপে যাচ্ছে। তোমাকে দূর থেকে দেখলেই বলবে, দাঁড়া না অরুকে আমি মজা দেখাচ্ছি। ভুঁইঞাকাকাকে বলে এমন মার খাওয়াব না, জীবনেও ভুলতে পারবে না।
তিথি তার সঙ্গে এতদিন নিজের কথাই বলেছে—সে কারও নিন্দামন্দে থাকে না। তুলির কোনও কথাই এতদিন বলেনি। আজ কি তিথি বুঝতে পেরেছে, সে উচ্ছিষ্ট খেয়ে বেড়ালে, তার অরুদাকে ছোট করা হয়। অরুদাকে বিশ্বাস করে সে কি তাকে নিজের মানুষ ভেবে ফেলেছে।
তিথি বলল, ঠিক আছে পরে কথা হবে। বলেই ছুট। একদণ্ড আর দাঁড়াল না। বাটিতে মুড়ি আর দুটো সন্দেশ নিয়ে এসে হাজির। ঘরে আলাদা তার কাঁসার গেলাস আছে, কুঁজো থেকে গেলাসে জল ভরে একটা টিপয়ে রেখে বলল, আমি যাচ্ছি অরুদা। দরজা খোলা রেখে উধাও হবে না। শেকল তুলে দিয়ে যাবে। কুকুর বিড়ালের উৎপাত আছে বোঝ না।
তারপর আর তিথি একদণ্ড দাঁড়াল না। বড় বেশি লাফিয়ে লাফিয়ে হাঁটে, লাফিয়ে লাফিয়ে দৌড়ায়। তিথি দৌড়ে মাঠ পার হয়ে লনের ভেতর ঢুকে গেল। অরু বাইরে দাঁড়িয়েছিল, তিথি একসময় পাঁচিলের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।
তার এখন তাড়াতাড়ি খেয়ে বের হয়ে যাওয়া দরকার। দেরি হলে বিশুদা, অমল, কমল সবাই তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। শহর থেকে মেজদা নতুন র্যাকেট নিয়ে এসেছে। কর্ক এনেছে এক ডজন। শীতের শেষাশেষি নদীর পাড়ে নেট টাঙিয়ে আজ থেকে ব্যাডমিন্টন খেলা শুরু হবে। সে সঙ্গে না থাকলে বাঁশ, খোনতা কে নিয়ে যাবে! সে একজন আমলার পুত্র, এ—কাজটা তারই করা উচিত।
গোলঘরে যাবার সময়ই ভাবল, তিথিকে বড় বড় কথা না বললেই পারত। তিথি খারাপ পেতে পারে। তিথি এভাবে বাবুদের উচ্ছিষ্ট খেয়েই বড় হয়ে উঠেছে। কেন যে মনে হল বাবাও তার উচ্ছিষ্টভোজী এবং সেও। তার মুখে অত বড় বড় কথা শোভা পায় না। তিথি তার কথা শুনে ভাগ্যিস হেসে ফেলেনি।
তারপরেই মনে হয় কাজ করলে মানুষ ছোট হয়ে যায় না। হাতে র্যাকেট নিয়ে সেও খেলবে। খেলার নামে তার মধ্যে ঘোর সৃষ্টি হয়। নদীর পাড়ে যখন তারা নেট টাঙিয়ে খেলছিল, তখন আর নিজেকে কিছুতেই খাটো ভাবতে পারেনি। ফেরার সময় মনে হল সে রাজ্য জয় করে ফিরছে।
তবে তুলি বাবাকে মিছে অভিযোগ করে মার খাওয়াবার পরিকল্পনা করছে, ভাবতেই ভারী দমে গেল। তুলির সঙ্গে যাও ইচ্ছে হয়েছিল, দেখা হলে একদিন কথা বলবে, তাও আর বোধহয় হবে না। কি বলতে কি ভেবে নেবে কে জানে। আর তুলিকে সে কী কথা বলবে? তুমি ভালো আছো? তুমি দেখতে খুব সুন্দর। খুব বোকা বোকা কথা! তুলির সঙ্গে কথা বলার মতো ভাষাই তার জানা নেই।
সবাই চলে গেছে, নদীর পাড়ে মানুষজন কমে আসছে, দূরে স্টিমারঘাটে গ্যাসবাতি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। ঘাটে যাত্রীদের ভিড় আছে। রাত আটটায় স্টিমার আসবে, যাত্রী নামবে, যাত্রী উঠবে। আশরাফ সারেঙ জাহাজ ভর্তি করে লোক তুলে নিয়ে যাবে। তার খুবই ইচ্ছে হয়েছিল, আশরাফ সারেঙের সঙ্গে ঘাটে গিয়ে একদিন দেখা করে। কিন্তু হয়ে ওঠে না। গোলঘরে তখন সবার সঙ্গে তাকেও পড়তে বসতে হয়। মাস্টারমশাই প্রাসাদের বড় বড় জানালা দেখিয়ে বলেন, এই হচ্ছে আয়তক্ষেত্র। ঘরের মেঝে দেখিয়ে বলেন, এই হল বর্গক্ষেত্র—যার চারটি বাহুই সমান।
পড়াশোনার পীড়নও কম নয়। ক্লাশে পড়া না পারলে ঠিক বাবার কানে কথা উঠে যায়।
ভুঁইঞামশায় আছেন?
দ্বিজপদ সার এসে হাজির।
তোমার বাবা কোথায়।
সে বুঝতে পারে দ্বিজপদ সার নালিশ জানাতে এসেছেন। সে দরজা খুলে সামনের বারান্দায় একটা টিনের চেয়ার বের করে দেয়। তারপর বাবাকে খুঁজে বেড়ায়। ইংরেজি গ্রামার ট্রানস্লেশনে সে কাঁচা, তার নাকি মনোযোগেরও অভাব আছে—দ্বিজপদ সার সে—সব কথা বলতেই হয়তো এসেছেন। সে তার বাবাকে খুঁজতে গিয়ে নিজেই হারিয়ে যায়।
এভাবে সে কতদিন কত কারণে নদীর পাড়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। কাছারিবাড়িতে ঢুকতে ইচ্ছে হয় না। বাড়ির জন্য মন কেমন করে তখন। পূজার ছুটিতে সে বাড়ি যেতে পারবে, পূজার তো এখনও অনেক দেরি। নতুন উপসর্গ তুলি। তাকে ভয় দেখিয়েছে, তুলি মিছে কথা বলে না। তুলি কাউকে ভয় পায় না। ভয় না পেলে যেন মিছে কথা বলা যায় না।
নদী থেকে হাওয়া উঠে আসছে। জোয়ারে নদীর জল বাড়ছে। দেখতে না দেখতে বর্ষা এসে যাবে। বর্ষায় নদী বিশেষ করে এই কোয়ালা নদীতে কুমির পর্যন্ত ভেসে আসে। তিথিই তাকে একদিন খবর দিয়েছিল, জমিদার হেমন্ত রায়চৌধুরীর বৈঠকখানার বারান্দায় শ্বেতপাথরের টেবিলে একটা কুমিরের ছাল আছে। তিথি তাকে সেখানে একদিন নিয়ে যাবে, এমনও কথা দিয়েছে।
নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকলে কত কথা মনে হয়। আর কত পাখির ওড়াউড়ি, কোথা থেকে আসে, কোথায় যায় সে কিছুই জানে না। বর্ষা এলে দু—পাড়ের চর ডুবে যায়। নদীর ঘাটগুলিতে যত সিঁড়ি আছে সব জলে ডুবে যায়। তিথিই সব খবর দেয় তাকে। কিন্তু তুলির খবরটা না দিলেই পারত। এমন সুন্দর মেয়েটা এত কুবুদ্ধির ডিপো ভাবতেই তার কষ্ট হচ্ছিল।
তবে বাবা তাকে কখনোই গায়ে হাত তোলেনি। বাবাকে বলে মার খাওয়ানো সহজ না। বাবা কি পুতুল! সে সাহস পায়। ঘাটলার সিঁড়ি থেকে উঠে দাঁড়ায়। আকাশ আর মেঘমালায় ঢেকে আছে চারপাশ। দুটো একটা নক্ষত্রের প্রতিবিম্ব জলে ভাসছে। ছলাত ছলাত জলের শব্দ। গুন টেনে নিয়ে যাচ্ছে মাঝিরা। কত দূর দেশে চলে যায় কত লোক। সেও চলে এসেছে—তিথির জন্যই হোক কিংবা এই গ্রাম, মাঠ, স্কুল, মজা খাল বিশাল সব প্রাসাদ আর বাবুদের জাঁকজমক, যেমন জমিদার হেমন্ত রায়চৌধুরীর আস্তাবলে বিশাল দুটো আরবি ঘোড়া এবং ঘোড়ায় চড়ে নদীর পাড় ধরে হরিশবাবুর ছোটা, যে না দেখেছে, সে জানেই না, এক আশ্চর্য অশ্বারোহী কদম দিতে দিতে বিন্দু থেকে বিন্দুবৎ হয়ে যেতে পারে। হরিশবাবু দেশে এলে তিথি তাকে নিয়ে নদীর পাড়ে ছুটে যাবেই কারণ হরিশবাবু বিকেলে ঘোড়ায় চড়ে নদীর পাড়ে হাওয়া খেতে বের হন। তিথি তাকে গোপনে একটা চিরকুট ধরিয়ে দেয়। চিরকুটে কী লেখা থাকে সে জানে না। তিথি চিরকুট হোক, চিঠি হোক খুবই গোপনে হরিশবাবুর হাতে দিয়ে দেয়। ঠিক ঘাটলার পাশে কদম দিতে দিতে তিথির সামনে এসে দাঁড়াবেন। তারপর ভারী সতর্ক নজর। ঘোড়ার উপরেই তিনি বসে থাকেন। নুয়ে তিথির চিঠিটা নিয়েই দিঘির পাড় ধরে অদৃশ্য হয়ে যান।
আসলে অরুর মাঝে মাঝে কেন জানি মনে হয় কোনও স্বপ্নের পৃথিবীতে সে এসে উঠেছে। বাড়ির জন্য প্রথম প্রথম খুবই মন খারাপ করত, কিন্তু দিন যত যাচ্ছে, তত তার মনে হয় মন খারাপ আর আগের মতো হয় না। সে তো দেখতে পায় তুলি সাটিনের ফ্রক গায় দিয়ে মাথায় সুন্দর লাল রিবন বেঁধে কখনও সুপারিবাগানে, কখনও নদীর চরে, ঘুরে বেড়াচ্ছে। সঙ্গে কেউ থাকে। সে কাছে থাকে না, ঝোপজঙ্গলের আড়াল থেকেই সে তুলিকে দেখতে বেশি ভালোবাসে। তুলি কাছাকাছি এলেই সে দৌড়ে পালায়—যদি তুলি টের পেয়ে যায়, সে চুরি করে চরের উপর একটা জ্যান্ত পরীর ওড়াউড়ি দেখছিল—ধরা পড়লে কেলেঙ্কারির একশেষ—সে না পালিয়ে থাকে কী করে!
তুলি মিছে কথা বলে না, তিথি ঠিকই বলেছে।
তুলি ঠিক টের পেয়েছে সে তাকে দেখে, তাকে দেখার জন্য নদীর পাড়ে কিংবা কাছারিবাড়ির বড় বড় আমগাছের আড়ালে সে দাঁড়িয়ে থাকে। কখনও বাবুদের সঙ্গে স্টিমারঘাটে গেলেও সে যে তুলির পিছু নেয়, তাও টের পেতে পারে। কখনোই তুলির সামনে যেতে সাহস পায়নি। রান্নাবাড়িতেই কখনও রাতে সে কাছ থেকে তুলিকে দেখতে পায়। রোজদিন দেখা হয় না। তুলি আগে খেয়ে নিলে দেখা হওয়ার কথাও নয়, তার যে কি হয়, সে রান্নাবাড়িতে মাথা নিচু করেই খায়। চোখে চোখ পড়ে গেলে কত বড় বেয়াদপি, সেটা সে বোঝে। তুলি অপছন্দও করতে পারে। বাড়ির একজন আমলার পুত্রের এত আস্পর্ধা হয় কী করে! সাটিনের ফ্রকের নিচে তুলি আজকাল টেপ দেওয়া জামাও পরে।
তুলির এত সে জানে, তুলি কেন জানবে না, তুলিকে দেখলেই সে পালায়।
কাছারিবাড়ির দিকে সে হেঁটে যাচ্ছে। বাবার সঙ্গে তার কমই দেখা হয়। বাবার ছুটিছাটা নেই। রবিবার শনিবার নেই। সেই আটটায় গিয়ে নাজিরখানায় বসেন, তক্তাপোশে সাদা ধবধবে ফরাস পাতা—দু—তিনটে তাকিয়া, সামনে কাঠের একটা বড় ক্যাশবাক্স, দেয়ালের দিকে গোটা দুই লম্বা টুল, লোকজন সব সময় বাবার কাছে বসেই থাকে—আদায়পত্র, কিছু সুদেরও কারবার আছে, নদী থেকে বড় রকমের রোজগার আছে বাবুদের—নদীর ডাক হয়—ইলিশমাছের জো পড়লে আদাইয়ের পরিমাণ বাড়ে।
সকালবেলাতেই ভেতর বাড়ি থেকে একটা লম্বা ফর্দ চলে আসে। বাবা ফর্দ মিলিয়ে সব কিছু নিয়ে আসার জন্য হরমোহনকে বাজারে পাঠিয়ে দেন। যার যা দরকার, বাবার কাছে দরকারমতো চিরকুট আসে। লম্বা খেরো খাতায় বাবা সব খরচখরচা এবং আদায় কী হল সব টাকার জমা খরচ তুলে রাখেন। সাঁজবেলায় দেবকুমারবাবু কিংবা নবকুমারবাবুর কাছে সারাদিনের খরচ খরচা এবং আয়ের হিসাব অর্থাৎ খেরো খাতাটি সম্বল করে বাবা তাদের কাছে চলে যান। মামলা মোকদ্দমা অথবা তালুকের প্রজাদের বাদবিসংবাদে বাবাকেই ছুটতে হয়।
যত তার কথা রাতে।
তোমার কোনও অসুবিধা হচ্ছে না তো অরু?
আজ্ঞে না।
বাড়ির জন্য মন খারাপ করছে না তো?
আজ্ঞে না।
মন দিয়ে লেখাপড়া করবে। পড়া বুঝতে না পারলে দ্বিজপদকে বলবে।
তখনই একদিন সে তার বাবাকে কেন যে বলল, আচ্ছা বাবা আমার জামাপ্যান্ট আমি কেচে নিতে পারি না।
পারো।
সকালে তিথির জল তুলে দিয়ে যাওয়ার কিন্তু দরকার হয় না। আমিই তুলে রাখতে পারি।
ইচ্ছে করলে সবই করা যায় অরু। এতে সাবলম্বী হওয়া যায়। সবকিছু নিজে করে নিতে পারার মতো বড় কিছু নেই।
আমি তিথিকে ঘরে ঢুকতে বারণ করে দেব।
কেন? সে কী করেছে।
কিছু করেনি। তিথির কত কাজ ভেতর বাড়িতে। সে সব করে কখন?
অঃ এই কথা। তবে তিথি কি দমবার পাত্র। আমার তো মনে হয় না রাজি করাতে পারবে।
বাবার কথাই ঠিক।
সে তিথিকে নিষেধ করেছিল।
শোন তিথি, এই কাজটুকু তোর না করলেও চলবে।
তিথি বড় বড় চোখে তাকিয়েছিল তার দিকে। যেন কিছুই বুঝতে পারছে না।
জলটল আমিই তুলে রাখব। বিছানা করে নিতে আমার অসুবিধা হবে না। জামাপ্যান্ট গোলা সাবানে কাচতে কতটুকু সময় লাগে বল।
ঠিক আছে করে নেবে। করতে পারলে তো ভালোই। তারপরই তিথি সিঁড়ি ধরে নামার সময় ভেংচি কেটে বলল, কত মুরদ। জানা আছে। তিনি সব করে নেবেন তা হলেই হয়েছে!
কিন্তু তিথি বোধহয় শেষে অবাকই হয়ে গেছিল, সে তো ছেড়ে দেবার জন্য বসে নেই। তিথি যখন দেখল, কোনও কাজেই তার ত্রুটি থাকছে না, কেমন দিন দিন বিমর্ষ হয়ে যেতে থাকল। স্কুলে যাবার সময় দেখতে পায় তিথি সিঁড়িতে গালে হাত দিয়ে বসে আছে, স্কুল থেকে ফিরেও দেখতে পায় গালে হাত দিয়ে বসে আছে। কাজের কোনও খুঁতই ধরতে পারছে না, ক্ষোভে কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। আর একদিন এসে দেখল, সারা ঘর তছনছ করে রেখেছে কে! মেঝেতে বালতির সব জল ঢেলে দিয়েছে কেউ। ঘরে ঢুকেই অরুর মাথা খারাপ। তিথির কাজ। তিথিই শেকল খুলে সব তছনছ করে দিয়ে গেছে। কাজ কেড়ে নেওয়ায় তার বোধ হয় সহ্য হচ্ছে না।
তিথি! তিথি!
সে দরজার বাইরে লাফিয়ে নেমে গেল।
তারপর তিথিদের বাড়ির দিকে ছুটল।
না কোথাও তিথি নেই।
কোথায় গেলে মেয়েটা?
অরণি কাউকে বলতেও পারছে না, আমার ঘর তিথি তছনছ করে দিয়েছে। বইটই পেনসিল খাতা সারা চকিময়। জলে ভাসছে মেঝে। কাঁসার ঘটি গেলাস গড়াগড়ি খাচ্ছে চকির নিচে। এটা যে তিথিরই কাজ বলে কি করে!
শেষে সে তিথিকে খুঁজে পেল সুপারিবাগানের ভেতর। গাছগুলো খুবই পাতলা, দূর থেকেও দেখা যায় ভেতরে কেউ বসে থাকলে। তখন সূর্য অস্ত যাচ্ছে নদীতে। নদীর জল তেমনি ছলাত ছলাত। পাড় ভাঙারও শব্দ পেল। হরিশবাবুর ঘোড়াও ছায়ার মতো দূরে ভেসে উঠল।
অরু ছুটে যাচ্ছে।
সুপারিবাগানের ভেতর দিয়ে সোজা ছোটা যায় না। সে এ—গাছ ও—গাছ ডাইনে বাঁয়ে ফেলে বাগানে ঢুকে যাচ্ছে।
আর ডাকছে, এই তিথি, এখানে লুকিয়ে থেকে রক্ষা পাবি ভাবছিস! তোর বাবাকে ডেকে সব না দেখাচ্ছি তো আমার নাম অরণি না। তোর এত জেদ!
এই কি, কাছে গিয়ে কী দেখছে!
তিথি গাছের গুঁড়িতে বসে আছে মাথা নিচু করে। ডাকলেও সাড়া দিচ্ছে না।
অরু জোর করে মুখ দেখার জন্য তিথিকে চিৎ করে দিল। তিথি বিন্দুমাত্র জোরাজুরি করল না। কারণ তিথি বোকার মতো ভেউ ভেউ করে কাঁদছে—আমি কী করব বলে দাও। আমি কী নিয়ে থাকব বলে দাও।
অরণি হতভম্ব। বুঝতে পারছে না, সে হাসবে না রাগ দেখাবে। আমি কী করব, কী নিয়ে থাকব—এত পাকা পাকা কথা মেয়েটার, এটুকুন মেয়ে কেমন সুন্দর সাজিয়ে গুছিয়ে কথা বলতে পারে। তিথির পক্ষেই সম্ভব?
নে ওঠ। ঘরে চল। যে হাতে সব তছনছ করেছিস সেই হাতে সব সাজিয়ে রাখ। স্টিমারঘাট থেকে বাবা ফিরে এলে মুশকিলে পড়ে যাবি।
তিথি হি হি করে হাসতে হাসতে উঠে বসল, তারপর ছুটতে থাকল, যেন সে জয়লাভ করে খুবই খুশি—ছোটার মধ্যে তিথির এত সজীবতা থাকে যে বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না। এক বিনুনি বাঁধা, মার্কিন কাপড়ের ঢোলা সেমিজ গায়ে, উসখোখুসকো চুলে মেয়েটার লাবণ্য যেন আরও বেড়ে যায় তখন। আর তখনই মনে হয়েছিল, তিথি চিৎ হয়ে পড়ে থেকে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল ঠিক, আবার সঙ্গে সঙ্গে এমন চোখে ওকে দেখছিল যেন কিছু একটা হয়ে যাক। আর কিছু না হোক, অরুদা তাকে আদর করলে সে আপত্তি করবে না।
এই সব মনে হলেই তিথির জন্য তার কষ্ট হয়। সে ধীরে ধীরে হাঁটে। তার কিছু ভালো লাগে না। অমলদা যাবার সময় তাকে ডেকে গেছে, এই অরু ঘাটলায় গিয়ে আবার বসলি কেন? পড়াশোনা নেই।
সে সাড়া দেয়নি। কিন্তু গোলঘরে সবাই পড়তে চলে যাবে। তাকেও হাতমুখ ধুয়ে মাস্টারমশাইর সামনে গিয়ে পড়তে বসতে হবে, সে না গেলে দাদারাই খুঁজতে বের হবে। কাছারিবাড়িতে এসে খুঁজবে তাকে।
সে পা চালিয়ে হাঁটছে। সুপারিবাগান পার হয়ে কাছারিবাড়ির মাঠে ঢুকতেই মনে হল কারা যেন মাঠে তার জন্য অপেক্ষা করছে। কাছে গেলে দেখল তিথি আর তুলি। তুলিকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে। তার সঙ্গে তুলির ভাব না হলে তিথি বোধহয় স্বস্তি পাচ্ছিল না।
তিথি বলল, কোথায় একা একা ঘুরছিলে। জানো সাঁজবেলায় তেঁতুলতলা দিয়ে কেউ আসে না। জায়গাটা ভালো না। একা একা তেঁতুলতলা দিয়ে চলে এলে!
আসলে রাস্তা সংক্ষিপ্ত করার জন্যই সে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে তেঁতুলতলার নিচ দিয়ে উঠে এসেছে। জায়গাটা যে ভালো না সেও শুনেছে। ছোটপিসিকে এখানে একবার ভূতে ধরেছিল—সাঁজ লাগলে রাস্তাটা দিয়ে কেউ বড় আসে না। তুলির আক্রোশের কথা ভাবতে গিয়ে এতই দমে গিয়েছিল, তার কোনও কিছুই প্রায় খেয়াল ছিল না। সেই তুলি অরুর পাশে দাঁড়িয়ে আছে ঠিক, তবে তাকে দেখছে না। আকাশের দিকে তাকিয়ে প্রিয় কোনও নক্ষত্র খুঁজে বেড়াচ্ছে যেন।
তিথি না পেরে বলল, এই ছোড়দি, অরুদাকে কী বলবে বলেছিলে?
কী বলব?
কেন, বললে না, চল তো, অরুর সঙ্গে আমার কথা আছে।
কখন বললাম?
জানি না বাপু, তা হলে আসার কী দরকার ছিল। অরুদা তুমি যাও। হাতমুখ ধুয়ে পড়তে বসোগে।
অরু যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। সে পা বাড়াতেই তুলি বলল, সেদিন মাঠের আড়ালে দাঁড়িয়ে কী দেখছিলে?
কবে?
মনে নেই তোমার। আমি চরের বালিতে বাণীপিসির সঙ্গে হাওয়া খাচ্ছিলাম।
অরু সোজাসুজি বলল, না। মনে নেই।
না, আচ্ছা নাই মানলাম। তারপরই বলল, আমি বাঘও নয় ভালুকও না। আমার সঙ্গে কথা বললে জাত যাবে না। কি মনে থাকবে?
কী কথা বলব?
কথার কি শেষ আছে। আমাকে চুরি করে দেখলে খুব রাগ হয় আমার জানো?
ঠিক আছে আর দেখব না।
তিথি বলল, তুমি ছোড়দিকে তবে সত্যি চুরি করে দ্যাখো!
কী বলব, ও যখন বলছে—
ও বললেই তুমি মেনে নেবে। এ কেমন কথা। চুরি করে দেখার কী আছে!
অরু কিছুটা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। এই চুরি করে দেখার মধ্যে কি কোনও অন্য অনুভূতি কাজ করে। সে বড় হয়ে যাচ্ছে। সে নিজেকে যতই আড়াল করে রাখুক তার ভেতর একজন নারী যে স্বপ্নে বড় হয়ে উঠছে বুঝতে পারে। এই সব গোপন কথা যদি সত্যি ফাঁস হয়ে যায়, তবে সে মুখ দেখাবে কী করে! বাবা যে তবে খুবই জলে পড়ে যাবেন। সেদিনের ছেলে, ক্লাশ এইটে সে পড়ে, তার মধ্যে একজন নারী স্বপ্নে বড় হয়ে উঠলে যে রোগব্যাধির পর্যায়ে পড়ে। কলঙ্কও কম না।
তখনই তুলি বলল, আমি কাউকে কিছু বলতে যাচ্ছি না। আমার পুতুলের বিয়ে আজ। তুমি খাবে। তিথি এসে তোমাকে নিয়ে যাবে। না গেলে রাগ করব।
পুতুলের বিয়ে নিয়ে অরুর এক ধন্দ। সে খাবে। কী খাবে? সে যাই হোক অরু বুঝল, সে তুলিকে দেখে যা ভাবে, তুলিও তাকে দেখলে তেমনই কিছু একটা ভাবে। তুলি তার বিরুদ্ধে খুব বেশি কিছু রটাতে সাহস পাবে না। তুলি নিজেও ভেতরে ভেতরে বড় হয়ে যাচ্ছে। তুলিও তার শরীর নিয়ে ঠিক কিছু ভাবে।
এভাবে সন্ধ্যার ম্লান অন্ধকারে অরুর মুখ রক্তাভ হয়ে গেল। ভেতরে এক অতীব স্পৃহা শরীরের কোষে কোষে ঢেউ তুলে দিচ্ছে। সে কোনওরকমে কাছারিবাড়িতে ঢুকে তক্তাপোষে বসে পড়ল।
হাতমুখ ধোয়ার কথা মনে থাকল না।
কেমন ভ্যাবলু বনে গেছে যেন।
মনে হয় তার জীবনে এই প্রথম এক পালতোলা নৌকা এসে হাজির। নৌকায় উঠে গেলেই এক রহস্যময় দেশ, শরীরে সুঘ্রাণ—হাতে পায়ে জংঘায় পদ্মফুলের ছড়াছড়ি। নরম পাপড়ি, কোমল ত্বকের ভিতর ফুটে থাকা নরম স্পর্শে তার শরীরে বিদ্যুৎ খেলে যাচ্ছে। সে হাত পা টান করে একটা বালিশ টেনে শুয়ে পড়ল। কেমন অসাড় হয়ে যাচ্ছে তার শরীর।
তখনই দ্বিজপদ সারকে অরুর নামে নালিশ।
সার দিন দিন অরু ফাঁকিবাজ হয়ে যাচ্ছে। এখনও তার আসার নামগন্ধ নেই। কখন পড়তে বসবে!
দ্বিজপদ বুঝতে পারেন, যতক্ষণ তিনি পড়ান, ততক্ষণ বাবুদের ছেলেরা হাজতখানায় বসে থাকে। অরু না আসায়, তাদের ক্ষোভ বাড়ছে। হাজতখানার আর এক কয়েদির পাত্তাই নেই। সার শুধু একবার বলেছিলেন, অরুর শরীর খারাপ।
কমল বলল, ডাহা ফাঁকিবাজ সার। পড়ার নামে মাথায় বাজ পড়ে। কী করছে, কাছারিবাড়িতে! দেখে আসব সার?
দ্বিজপদ হাসলেন। আসলে পড়া থেকে ফাঁকি দেবার সুযোগ খুঁজছে। ভুঁইঞামশায়ের পুত্রটি পড়াশোনায় বেশ ভালো। পড়াশোনায় অরুর যথেষ্ট আগ্রহও আছে। যথাসময়েই সে চলে আসে। দ্বিজপদ ঘরে ঢুকে আর কাউকে দেখতে না পেলেও, অরুকে দেখতে পান। দ্বিজপদ ঘরে ঢুকলে সে উঠে দাঁড়ায়। নম্র স্বভাবের ছেলেটির পড়াশোনার ভার ভুঁইঞামশায় তার হাতেই ছেড়ে দিয়েছেন, সে যদি না আসে, চিন্তারই কারণ। আমবাগানের এক কোনায় কাছারিবাড়িতে একাই তাকে থাকতে হয়। দ্বিজপদ কী ভেবে বললেন, ঠিক আছে। আমিই দেখে আসছি।
এতে সবাই একবাক্যে সায় দিল, সেই ভালো সার।
অর্থাৎ তিনি যতক্ষণ না থাকবেন, ততক্ষণই তাদের রেহাই।
বিশু বলল, আমি যাব সঙ্গে।
কী দরকার!
কমল বলল, টর্চ নিলেন না?
তা সাপখোপের উপদ্রব আছে। নদীর পাড়ে বাড়ি। ঝোপজঙ্গল, কোথাও কোথাও প্রাসাদের ধ্বংসস্তূপও আছে। বিষধর ভুজঙ্গের উৎপাতও কম না। তিনি কী ভেবে টর্চ বাতিটা সঙ্গেই নিলেন।
ঘর থেকে বের হলেই দুটো করবীফুলের গাছ, তারপর একটা হাসনুহানার গাছ। গাছটায় দু—একটাই ফুল ফোটে। ফুলের তীব্র গন্ধ ছড়ালেই বোঝেন, গাছে কোথাও ফুল ফুটেছে। গাছটা মাথায় আনারসের ডিগের মতো লম্বা ঘন পাতায় ঝোপ সৃষ্টি করে রেখেছে। গাছটার নিচ দিয়ে যাবার সময় তিনি খুব সতর্ক থাকেন। কেন যে মনে হয় যে—কোনও মুহূর্তে পাতার ঝোপ থেকে পোকামাকড় লাফিয়ে পড়বে। খুবই দুর্লভ ফুলের গাছ। দিনের বেলাতেও ফুল খুঁজে বের করা কঠিন—অথচ ফুল যে ফুটেছে, গন্ধেই টের পাওয়া যায়। বিষধর সাপেদের বড় প্রিয় এই ফুলের ঘ্রাণ। একেবারে রাস্তার উপর গাছটা জমিদারবাবুরা না লাগালেই পারতেন। তিনি কী ভেবে গাছটার নিচে ঢুকে যাবার আগে টর্চ মেরেও দেখলেন। প্রায় বিশাল ছত্রাকার হয়ে আছে গাছের মাথাটি। ঘন সবুজের সমারোহ।
গাছটা পার হলেই সবুজ লন। শীত বসন্তে নীল রঙের বেতের চেয়ার টেবিল পাতা থাকে। বাবুরা বিকালে হাওয়া খান এখানটায় বসে। নদীর জলে নৌকা ভাসে। রাতে স্টিমারের সার্চলাইটে কেমন নীলাভ দেখায় এলাকাটা। বাবুদের আত্মীয়স্বজনও কম না। এখানে বসে তাস পাশার আড্ডাও জমিয়ে তোলার ব্যবস্থা থাকে।
দ্বিজপদ যাচ্ছিলেন, তার ছাত্রটি কাছারিবাড়িতে একা একা কী করছে, শরীর যদি খারাপ হয়, এই সব ভেবেই আমবাগানে ঢুকে গেলেন। এক ইটের দেয়াল, মাথায় টিনের চাল, আটচালার উপরে গাছের ডালপাতায় জায়গাটা খুবই অন্ধকার হয়ে আছে। মূল বাড়ি থেকে বড়ই আলগা কাছারিবাড়িটা। অরু ছেলেমানুষ সে এমন একটি পরিত্যক্ত জায়গায় একা বসে থাকতেও ভয় পাবে।
সে কি ঘরে নেই?
দরজা খোলা?
টর্চ মেরে দূর থেকেই সব টের পাচ্ছেন।
কেউ হারিকেনও জ্বালিয়ে দিয়ে যায়নি।
দ্বিজপদ কিছুটা দ্রুতই হেঁটে যেতে থাকলেন।
ঘরে ঢোকার আগে ডাকলেন, অরু আছিস! অরু।
কোনও সাড়া নেই।
তাজ্জব। ছেলেটা গেল কোথায়?
ভেতরে টর্চ মারতেই দেখলেন, অরু শুয়ে আছে একটা লম্বা সাদা চাদরে মুখ মাথা ঢেকে। সে কি ঘুমোচ্ছে!
এই অসময়ে!
এই অরু, অরু।
অরু ধড়ফড় করে উঠে বসল।
ঘর অন্ধকার করে শুয়ে আছিস, কী ব্যাপার, শরীর খারাপ!
টর্চের আলো চোখে পড়ায়, অরু তাকাতে পারছিল না। সে হাতে চোখ আড়াল করে বোঝার চেষ্টা করল, কে তাকে ডাকছে!
তার যে কী হয়েছিল! সে কী বলবে। লজ্জায় মাথা নিচু করে বসে থাকা ছাড়া তার যেন আর অন্য কোনও উপায় নেই। সার নিজে চলে এসেছেন। এতে সে আরও শঙ্কিত হয়ে উঠল। সে ঘরে কখন ঢুকে গেছে, কখন চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েছিল—শরীরে তার যেন কীসের ঘোর উপস্থিত। চোখ মুখ জ্বালা করছিল, এবং শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে আশ্চর্য এক ঝড়ের আভাস। ঝড়ে তাকে বড়ই বিপর্যস্ত করে দিয়ে গেছে—সে কিছুটা যেন চৈতন্যও হারিয়েছিল—এক গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত পৃথিবীতে সে স্বপ্নের বালিহাঁস হয়ে গেছিল। কোনও শিকারের দৃশ্য, সে মজবুত হাতে হাঁসটার ডানা, কিংবা পালক ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেয়েছে।
লজ্জায় সে কথা বলতে পারছিল না।
কী হয়েছে? শরীর খারাপ অরু?
আজ্ঞে। সে কথা বলতে পারছে না।
ভয় পেয়েছিস?
আজ্ঞে… সে কথা বলতে পারছে না।
ঘরে হারিকেনও জ্বালিসনি!
আজ্ঞে আমি যাচ্ছি সার।
আয়। তোর একা থাকতে ভয় করলে, কারও এ—ঘরে থাকা দরকার। সত্যি তো, তুই থাকিস কী করে। ঠিক আছে, ভুঁইঞামশায়কে বলছি।
আজ্ঞে না সার বলবেন না। আমার একা থাকতে ভয় করে না। আপনি বাবাকে কিছু বলবেন না।
হারিকেন ধরা।
সে চকি থেকে নেমে হারিকেন ধরাল।
এখন তার ধীরে ধীরে সবই মনে পড়ছে। তিথি হারিকেনের চিমনি মুছে তেল ভরে রেখে গেছে। দরকারে সে জ্বালিয়ে নেয়। নিবিয়ে দেয়। আজ ঘরে ঢুকে কিছুই মনে ছিল না। শরীরে ঘোর উপস্থিত হলে এমনই বুঝি হয়—সে তার দ্বিতীয় সত্তা আবিষ্কার করে কেমন নির্বোধ হয়ে গেছে আজ।
সে খুবই ধীর পায়ে বই খাতা নিয়ে ঘর থেকে বের হবার আগে আলো কমিয়ে দিল হারিকেনের। তারপর দ্বিজপদ সারের পিছনে প্রায় চোরের মতো হেঁটে যেতে থাকল। তার মনেই থাকল না, তুলি তার পুতুলের বিয়েতে খেতে বলেছে। বড়লোকের মেয়ে তুলি, তার পুতুলের বিয়ে—সেখানে একমাত্র নিমন্ত্রিত অতিথি বোধহয় সেই ছিল। কারণ সকালে তিথির গালিগালাজে প্রায় ভূত ভেগে যাওয়ার মতো অবস্থা। তুমি কী অরুদা! ছোড়দি কত আশা নিয়ে বসেছিল, তোমাকে সে সামনে বসিয়ে লুচি পায়েস খাওয়াবে। তুমি পাত্তাই দিলে না। ভুঁইঞাকাকার সঙ্গে রান্নাবাড়িতে খেতে ঢুকে গেলে! তোমার কপালে অনেক দুঃখ আছে।
অরু খেপে গিয়ে বলল, আমার কপালে না তোর কপালে!
বারে, আমার কী দোষ!
হরিশবাবুকে ছোটপিসির চিরকুট গোপনে পাচার করিস, ওটা বুঝি দোষ না।
তুমি অরুদা নিষ্ঠুর। জানো, ছোটপিসি বালবিধবা?
জানব না কেন? তাই বলে তোকে দিয়ে চিঠি পাচার করাবে! জানতে পারলে তোর কী হবে জানিস?
কী হবে?
অন্দর থেকে তোকে বাবুরা তাড়াবে।
জানবেই না, জানতে দেবই না। তুমি ছাড়া আর কেউ যে জানে না।
চিঠিতে কী লেখা থাকে জানিস?
হ্যাঁ, জানি।
বড় অকপটে তিথি স্বীকার করে ফেলল।
কী লেখা থাকে বল তো!
স্বপ্নের কথা লেখা থাকে। জানো স্বপ্নের কথা পড়তে নেই, পড়লে অভিশাপে পাথর হয়ে যেতে হয়। আমি পাথর হয়ে যাই, তুমি কি চাও?
তারপর তিথি আর দাঁড়াল না। সুপারিবাগান পার হয়ে নদীর চড়ায় কাশবনের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল। কেন যে গেল! তিথি কী চায়! সে কিছুটা দৌড়ে গিয়েও ফিরে এল। তার সাহস নেই। তিথির সঙ্গে নদীর চরে কাশের জঙ্গলে হারিয়ে গেলে বড় পাপ কাজ হবে। সে ধীরে ধীরে কাছারিবাড়িতে উঠে গেল।