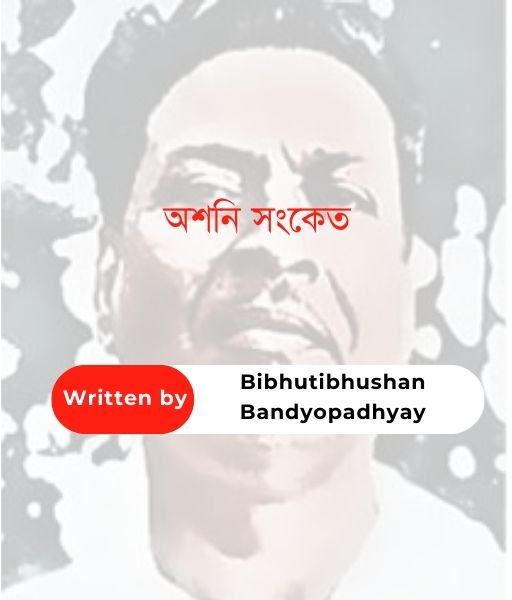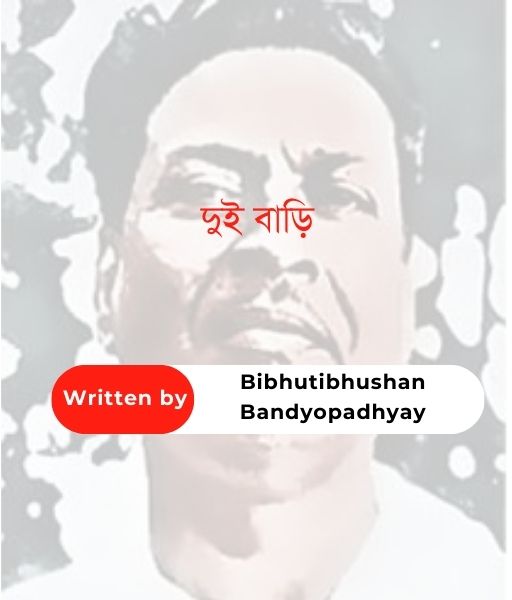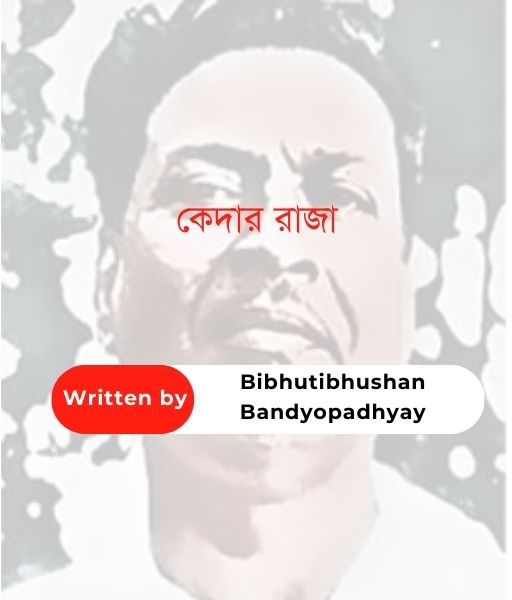Chander Pahar – প্রথম পরিচ্ছেদ
শঙ্কর একেবারে অজ পাড়াগাঁয়ের ছেলে। এইবার সে সবে এফ.এ. পাশ দিয়ে গ্রামে বসেছে। কাজের মধ্যে সকালে বন্ধুবান্ধবদের বাড়িতে গিয়ে আড্ডা দেওয়া, দুপুরে আহারান্তে লম্বা ঘুম, বিকেলে পালঘাটের বাঁওড়ে মাছ ধরতে যাওয়া।
সারা বৈশাখ এইভাবে কাটবার পরে একদিন তার মা ডেকে বললেন— শোন একটা কথা বলি শঙ্কর। তোর বাবার শরীর ভালো নয়। এ অবস্থায় আর তোর পড়াশুনো হবে কী করে? কে খরচ দেবে? এইবার একটা কিছু কাজের চেষ্টা দ্যাখ।
মায়ের কথাটা শঙ্করকে ভাবিয়ে তুললে। সত্যিই তার বাবার শরীর আজ ক’মাস থেকে খুব খারাপ যাচ্ছে। কলকাতার খরচ দেওয়া তাঁর পক্ষে ক্রমেই অসম্ভব হয়ে উঠছে। অথচ করবেই বা কী শঙ্কর? এখন কি তাকে কেউ চাকুরি দেবে? চেনেই বা সে কাকে?
আমরা যে সময়ের কথা বলছি, ইউরোপের মহাযুদ্ধ বাধতে তখনও পাঁচ বছর দেরি। ১৯০৯ সালের কথা। তখন চাকুরির বাজার এতটা খারাপ ছিল না। শঙ্করদের গ্রামের এক ভদ্রলোক শ্যামনগরে না নৈহাটিতে পাটের কলে চাকুরি করতেন। শঙ্করের মা তাঁর স্ত্রীকে ছেলের চাকুরির কথা বলে এলেন, যাতে তিনি স্বামীকে বলে শঙ্করের জন্যে পাটের কলে একটা কাজ যোগাড় করে দিতে পারেন। ভদ্রলোক পরদিন বাড়ি বয়ে বলতে এলেন যে শঙ্করের চাকুরির জন্যে তিনি চেষ্টা করবেন।
শঙ্কর সাধারণ ধরণের ছেলে নয়। স্কুলে পড়বার সময় সে বরাবর খেলাধুলোতে প্রথম হয়ে এসেছে। সেবার মহকুমার এক্জিবিশনের সময় হাইজাম্পে সে প্রথম স্থান অধিকার করে মেডেল পায়। ফুটবলে অমন সেন্টার ফরওয়ার্ড ও অঞ্চলে তখন কেউ ছিল না। সাঁতার দিতে তার জুড়ি খুঁজে মেলা ভার। গাছে উঠতে, ঘোড়ায় চড়তে, বক্সিং-এ সে অত্যন্ত নিপুণ। কলকাতায় পড়বার সময় ওয়াই.এম.সি.এ. তে সে রীতিমতো বক্সিং অভ্যাস করেছে। এই সব কারণে পরীক্ষায় সে তত ভালো করতে পারেনি, দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছিল।
কিন্তু তার একটি বিষয়ে অদ্ভুত জ্ঞান ছিল। তার বাতিক ছিল যত রাজ্যের ম্যাপ ঘাঁটা ও বড় বড় ভূগোলের বই পড়া। ভূগোলের অঙ্ক কষতে সে খুব মজবুত। আমাদের দেশের আকাশে যে সব নক্ষত্রমণ্ডলী ওঠে, তা সে প্রায় সবই চেনে— ওটা কালপুরুষ, ওটা সপ্তর্ষি, ওটা ক্যাসিওপিয়া, ওটা বৃশ্চিক। কোন মাসে কোনটা ওঠে, কোন দিকে ওঠে— সব ওর নখদর্পণে। আকাশের দিকে চেয়ে তখুনি বলে দেবে। আমাদের দেশের বেশি ছেলে যে এসব জানে না, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে।
এবার পরীক্ষা দিয়ে কলকাতা থেকে আসবার সময় সে একরাশ ওই সব বই কিনে এনেছে, নির্জনে বসে প্রায়ই পড়ে আর কী ভাবে ওই জানে। তারপর এল তার বাবার অসুখ, সংসারের দারিদ্র্য এবং সঙ্গে সঙ্গে মায়ের মুখে পাটকলে চাকুরি নেওয়ার জন্যে অনুরোধ। কী করবে সে? সে নিতান্ত নিরুপায়। মা-বাপের মলিন মুখ সে দেখতে পারবে না। অগত্যা তাকে পাটের কলেই চাকুরি নিতে হবে। কিন্তু জীবনের স্বপ্ন তাহলে ভেঙে যাবে, তাও সে যে না বোঝে এমন নয়। ফুটবলের নাম করা সেন্টার ফরওয়ার্ড, জেলার হাইজাম্প চ্যাম্পিয়ান, নামজাদা সাঁতারু শঙ্কর হবে কিনা শেষে পাটের কলের বাবু; নিকেলের বইয়ের আকারের কৌটোতে খাবার কি পান নিয়ে ঝাড়ন পকেটে করে তাকে সকালের ভোঁ বাজতেই ছুটতে হবে কলে, আবার বারোটার সময় এসে দুটো খেয়ে নিয়েই আবার রওনা— ওদিকে সেই ছ’টার ভোঁ বাজলে ছুটি। তার তরুণ তাজা মন এর কথা ভাবতেই পারে না যে। ভাবতে গেলেই তার সারা দেহ-মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে— রেসের ঘোড়া শেষকালে ছ্যাকরা গাড়ি টানতে যাবে?
সন্ধ্যার বেশি দেরি নেই। নদীর ধারে নির্জনে বসে-বসে শঙ্কর এইসব কথাই ভাবছিল। তার মন উড়ে যেতে চায় পৃথিবীর দূর, দূর দেশে— শত দুঃসাহসিক কাজের মাঝখানে। লিভিংস্টোন, স্ট্যানলির মতো, হ্যারি জনস্টন, মার্কো পোলো, রবিনসন ক্রুসোর মতো। এর জন্যে ছেলেবেলা থেকে সে নিজেকে তৈরি করেছে— যদিও এ কথা ভেবে দেখেনি অন্য দেশের ছেলেদের পক্ষে যা ঘটতে পারে, বাঙালী ছেলেদের পক্ষে তা ঘটা এক রকম অসম্ভব। তারা তৈরি হয়েছে কেরানি, স্কুলমাস্টার, ডাক্তার বা উকিল হবার জন্যে। অজ্ঞাত অঞ্চলের অজ্ঞাত পথে পাড়ি দেওয়ার আশা তাদের পক্ষে নিতান্তই দুরাশা।
প্রদীপের মৃদু আলোয় সেদিন রাত্রে সে ওয়েস্টমার্কের বড় ভূগোলের বইখানা খুলে পড়তে বসল। এই বইখানার একটা জায়গা তাকে বড় মুগ্ধ করে। সেটা হচ্ছে প্রসিদ্ধ জার্মান পর্যটক অ্যাণ্টন হাউপ্টমান লিখিত আফ্রিকার একটা বড় পর্বত— মাউনটেন অফ দি মুন (চাঁদের পাহাড়) আরোহণের অদ্ভুত বিবরণ। কতবার সে এটা পড়েছে। পড়বার সময় কতবার ভেবেছে হের হাউপ্টমানের মতো সেও একদিন যাবে মাউনটেন অফ দি মুন জয় করতে।
স্বপ্ন! সত্যিকার চাঁদের পাহাড় দূরের জিনিসই চিরকাল। চাঁদের পাহাড় বুঝি পৃথিবীতে নামে?
সে রাত্রে বড় অদ্ভুত একটা স্বপ্ন দেখল সে…
চারধারে ঘন বাঁশের জঙ্গল। বুনো হাতির দল মড় মড় করে বাঁশ ভাঙছে। সে আর একজন কে তার সঙ্গে, দু’জনে একটা প্রকাণ্ড পাহাড়ে উঠছে, চারধারের দৃশ্য ঠিক হাউপ্টমানের লেখা মাউনটেন অফ দি মুনের দৃশ্যের মতো। সেই ঘন বাঁশ বন, সেই পরগাছা ঝোলানো বড় বড় গাছ, নিচে পচাপাতার রাশ, মাঝে মাঝে পাহাড়ের খালি গা, আর দূরে গাছপালার ফাঁকে জ্যোৎস্নায় ধোয়া সাদা ধবধবে চিরতূষারে ঢাকা পর্বতশিখরটি— এক একবার দেখা যাচ্ছে, এক একবার বনের আড়ালে চাপা পড়ছে। পরিষ্কার আকাশে দু-একটি তারা এখানে ওখানে। একবার সত্যিই সে যেন বুনো হাতির গর্জন শুনতে পেলে। সমস্ত বনটা কেঁপে উঠল… এত বাস্তব বলে মনে হল সেটা, যেন সেই ডাকেই তার ঘুম ভেঙে গেল! বিছানার উপর উঠে বসল, ভোর হয়ে গিয়েছে, জানালার ফাঁক দিয়ে দিনের আলো ঘরের মধ্যে এসেছে।
উঃ, কি স্বপ্নটাই দেখেছে সে! ভোরের স্বপ্ন নাকি সত্যি হয়, বলে তো অনেকে।
অনেকদিন আগের একটি ভাঙা পুরনো মন্দির আছে তাদের গাঁয়ে। বার ভূঁইয়ার এক ভূঁইয়ার জামাই মদন রায় নাকি প্রাচীন দিনে এই মন্দির তৈরি করেন। এখন মদন রায়ের বংশে কেউ নেই। মন্দির ভেঙেচুরে গিয়েছে, অশ্বত্থ গাছ, বটগাছ গজিয়েছে কার্নিসে— কিন্তু যেখানে ঠাকুরের বেদী তার উপরের খিলেনটা এখনো ঠিক আছে। কোনো মূর্তি নেই, তবুও শনি-মঙ্গলবারে পূজো হয়, মেয়েরা বেদীতে সিঁদুর-চন্দন মাখিয়ে রেখে যায়। সবাই বলে ঠাকুর বড় জাগ্রত, যে যা মানত করে তাই হয়। শঙ্কর সেদিন স্নান করে উঠে মন্দিরের একটা বটের ঝুরির গায়ে একটা ঢিল ঝুলিয়ে কি প্রার্থনা জানিয়ে এলে।
বিকেলে সে গিয়ে অনেকক্ষণ মন্দিরের সামনে দূর্বাঘাসের বনে বসে রইল। জায়গাটা পাড়ার মধ্যে হলেও বনে ঘেরা, কাছেই একটা পোড়ো বাড়ি; এদের বাড়িতে একটা খুন হয়ে গিয়েছিল শঙ্করের শিশুকালে— সেই থেকে বাড়ির মালিক এ গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র বাস করছেন; সবাই বলে জায়গাটায় ভূতের ভয়। একা কেউ এদিকে আসে না। শঙ্করের কিন্তু এই নির্জন মন্দির প্রাঙ্গণের নিরালা বনে চুপ করে বসে থাকতে বড় ভালো লাগে।
ওর মনে আজ ভোরের স্বপ্নটা দাগ কেটে বসে গিয়েছে। এই বনের মধ্যে বসে শঙ্করের আবার সেই ছবিটা মনে পড়ল— সেই মড় মড় করে বাঁশঝাড় ভাঙছে বুনো হাতির দল, পাহাড়ের অধিত্যকার নিবিড় বনে পাতা-লতার ফাঁকে ফাঁকে অনেক উঁচুতে পর্বতের জ্যোৎস্নাপাণ্ডুর তুষারাবৃত শিখরদেশটা যেন কোন স্বপ্নরাজ্যের সীমা নির্দেশ করছে। কত স্বপ্ন তো সে দেখেছে জীবনে— অত সুস্পষ্ট ছবি স্বপ্নে সে দেখেনি কখনো— এমন গভীর রেখাপাত করেনি কোনো স্বপ্ন তার মনে।
সব মিথ্যে! তাকে যেতে হবে পাটের কলে চাকরি করতে। তাই তার ললাট-লিপি, নয় কি?
কিন্তু মানুষের জীবনে এমন সব অদ্ভুত ঘটনা ঘটে যা উপন্যাসে ঘটাতে গেলে পাঠকেরা বিশ্বাস করতে চাইবে না, হেসেই উড়িয়ে দেবে। শঙ্করের জীবনেও এমন একটি ঘটনা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে ঘটে গেল।
সকালবেলা সে একটু নদীর ধারে বেড়িয়ে এসে সবে বাড়িতে পা দিয়েছে, এমন সময় ওপাড়ার রামেশ্বর মুখুয্যের স্ত্রী একটুকরো কাগজ নিয়ে এসে তার হাতে দিয়ে বললেন— বাবা শঙ্কর, আমার জামায়ের খোঁজ পাওয়া গেছে অনেকদিন পরে। ভদ্রেশ্বরে ওদের বাড়িতে চিঠি দিয়েছে, কাল পিন্টু সেখান থেকে এসেছে, এই তার ঠিকানা তারা লিখে দিয়েছে। পড় তো বাবা।
শঙ্কর বললে— উঃ, প্রায় দু’বছরের পর খোঁজ মিলল। বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে কি ভয়টাই দেখালেন। এর আগেও তো একবার পালিয়ে গিয়েছিলেন— না? তারপর সে কাগজটা খুললে। লেখা আছে—
প্রসাদদাস বন্দ্যোপাধ্যায়,
ইউগাণ্ডা রেলওয়ে হেড অফিস, কনস্ট্রাকশন ডিপার্টমেন্ট,
মোম্বাসা, পূর্ব-আফ্রিকা।
শঙ্করের হাত থেকে কাগজের টুকরোটা পড়ে গেল। পূর্ব-আফ্রিকা! পালিয়ে মানুষে এতদূর যায়? তবে সে জানে ননীবালা দিদির এই স্বামী অত্যন্ত একরোখা ডানপিটে ও ভবঘুরে ধরণের। একবার এই গ্রামেই তার সঙ্গে শঙ্করের আলাপও হয়েছিল— শঙ্কর তখন এন্ট্রান্স ক্লাসে সবে উঠেছে। লোকটা খুব উদার প্রকৃতির, লেখাপড়া ভালোই জানে, তবে কোনো একটা চাকুরিতে বেশিদিন টিকে থাকতে পারে না, উড়ে বেড়ানো স্বভাব। আর একবার পালিয়ে বর্মা না কোচিন কোথায় যেন গিয়েছিল। এবারও বড়দাদার সঙ্গে কি নিয়ে মনোমালিন্য হওয়ার দরুন বাড়ি থেকে পালিয়েছিল— এ খবর শঙ্কর আগেই শুনেছিল। সেই প্রসাদবাবু পালিয়ে গিয়ে ঠেলে উঠেছেন একেবারে পূর্ব-আফ্রিকায়!
রামেশ্বর মুখুয্যের স্ত্রী ভালো বুঝতে পারলেন না তাঁর জামাই কত দূরে গিয়েছে। অতটা দূরত্বের তাঁর ধারনা ছিল না। তিনি চলে গেলে শঙ্কর ঠিকানাটা নিজের নোট বইয়ে লিখে রাখলে এবং সেই সপ্তাহের মধ্যেই প্রসাদবাবুকে একখানা চিঠি দিলে। শঙ্করকে তাঁর মনে আছে কি? তাঁর শ্বশুরবাড়ির গাঁয়ের ছেলে সে। এবার এফ.এ. পাশ দিয়ে বাড়িতে বসে আছে। তিনি কি একটা চাকুরি করে দিতে পারেন তাঁদের রেলের মধ্যে? যতদূরে হয় সে যাবে।
দেড়মাস পরে, যখন শঙ্কর প্রায় হতাশ হয়ে পড়েছে চিঠির উত্তর প্রাপ্তি সম্বন্ধে— তখন একখানা খামের চিঠি এল শঙ্করের নামে। তাতে লেখা আছে—
মোম্বাসা
২ নং পোর্ট স্ট্রীট
প্রিয় শঙ্কর,
তোমার পত্র পেয়েছি। তোমাকে আমার খুব মনে আছে। কব্জির জোরে তোমার কাছে সেবার হেরে গিয়েছিলুম, সে কথা ভুলিনি। তুমি আসবে এখানে? চলে এসো। তোমার মতো ছেলে যদি বাইরে না বেরুবে তবে কে আর বেরুবে? এখানে নতুন রেল তৈরি হচ্ছে, আরও লোক নেবে। যত তাড়াতাড়ি পারো এসো। তোমার কাজ জুটিয়ে দেবার ভার আমি নিচ্ছি।
তোমাদের—
প্রসাদদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
শঙ্করের বাবা চিঠি দেখে খুব খুশি। যৌবনে তিনি নিজেও ছিলেন ডানপিটে ধরণের লোক। ছেলে পাটের কলে চাকুরি করতে যাবে এতে তাঁর মত ছিল না, শুধু সংসারের অভাব অনটনের দরুন শঙ্করের মায়ের মতেই সায় দিতে বাধ্য হয়েছিলেন।
এর মাস খানেক পরে শঙ্করের নামে এক টেলিগ্রাম এল ভদ্রেশ্বর থেকে। সেই জামাইটি দেশে এসেছেন সম্প্রতি। শঙ্কর যেন গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে টেলিগ্রাম পেয়েই। তিনি আবার মোম্বাসায় ফিরবেন দিন কুড়ির মধ্যে। শঙ্করকে তাহলে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারেন।