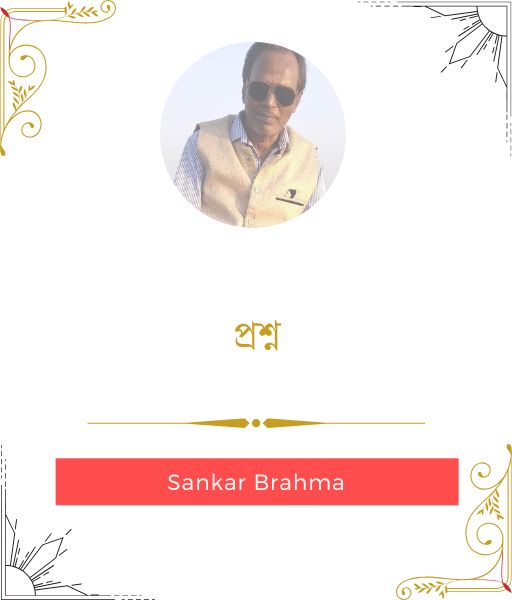কীর্তন গান
প্রাচীনকাল থেকেই ভারতীয় উপমহাদেশে, সঙ্গীতের দুটি ধারা – মার্গসঙ্গীত ও দেশীসঙ্গীত।
বর্তমানে প্রচলিত রাগসঙ্গীত বা উচ্চাঙ্গসঙ্গীত মার্গসঙ্গীতের অনুসারী। মার্গসঙ্গীতে রাগরূপায়ণ ও সুরের ভূমিকাই মুখ্য, কথার আবেদন সেখানে গৌণ। আর দেশীসঙ্গীত কথা ও সুর উভয়কেই প্রাধান্য দিয়েছে এবং তা একরৈখিক সুরের(melody) পথে বিবর্তিত ও বিকশিত হয়েছে। বাংলা সঙ্গীত প্রধানতঃ দেশীসঙ্গীতের আদর্শেই রচিত ও বিকশিত।
বাংলা ভাষা ও সঙ্গীতের প্রাচীন নিদর্শন চর্যাপদ। ১৯০৭ সালে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালের রাজগ্রন্থাগার থেকে এর পুঁথি আবিষ্কার করেন। আবিষ্কৃত পুঁথিটির নাম ‘চর্যাশ্চর্যবিনিশ্চয়’।’চর্যাশ্চর্যবিনিশ্চয়’ পুঁথিটি মোট ৪৭টি গানের সংকলন। খ্রিস্টীয় নবম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে গানগুলি রচিত।
চর্যাগীতিতে ব্যবহৃত রাগসমূহের কয়েকটি জয়দেবের গীতগোবিন্দম্ এবং বড়ু চন্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও লক্ষ্য করা যায়। চর্যার রামক্রী, গীতগোবিন্দে হয়েছে রামকিরি এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে দেশাখ। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ধানুষী (ধানশ্রী) মূলত চর্যাগীতির ধনাসী রাগের পরিবর্তিত রূপ। মলারী রাগ মল্লার নামে আজও সুপরিচিত। বর্তমানকালের রাগসঙ্গীতে এখনও প্রচলিত আছে গীতগোবিন্দম্-এ ব্যবহৃত কয়েকটি রাগ, যেমন ভৈরবী, বিভাস, বসন্ত, দেশ প্রভৃতি। তবে সে সময়ের রাগরূপায়ণ ও বর্তমানে প্রচলিত রাগলক্ষ্মণ একই রকম কিনা তা অবশ্য জানা যায় না। বিভাস রাগ এখন রাগসঙ্গীতে ভৈরব ঠাটের অন্তর্গত। আবার বাংলাদেশে শুদ্ধস্বরের বিভাস রাগ আছে, যা লোকসুরে বিশেষভাবে প্রচলিত।
গীতগোবিন্দম্-এ যেসব তালের উলেখ আছে, বাংলা কীর্তনে এখনও তার পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলাদেশে যে কর্ণাট রাগের ব্যবহার আছে, রাগতরঙ্গিণী গ্রন্থে তার উলেখ আছে। বাংলা কীর্তন গানে কর্ণাট রাগের বহুল প্রয়োগ হয়।
গীতগোবিন্দম্-এর দুটি প্রধান গায়নরূপ প্রচলিত ছিল একটি ধ্রুপদাঙ্গ, অন্যটি কীর্তনাঙ্গ। তবে গীতগোবিন্দম্ প্রধানত ধ্রুপদাঙ্গেই গীত হতো। বঙ্গদেশে গীতগোবিন্দম্-এর প্রভাব বিলুপ্ত হওয়ার পর শ্রীচৈতন্যের প্রভাবে কীর্তন আন্দোলন শুরু হয় এবং তাঁর অনুসারীরা কীর্তনের ঢঙে জয়দেবের গীতগোবিন্দম্ গাইতে থাকে। ফলে গীতগোবিন্দম্-এর পদগুলি কীর্তনে রূপান্তরিত হতে থাকে। এভাবে বাংলা কীর্তন গানে গীতগোবিন্দম্-এর প্রভাব গভীর ভাবে পড়ে।
বড়ু চন্ডীদাসের ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ বাংলা সঙ্গীতকলার উৎকৃষ্ট নিদর্শন । কাব্যসঙ্গীত এবং গীতিনাট্য উভয় দিক থেকেই গ্রন্থটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মনে করা হয় এর মধ্যে নৃত্যেরও পরিকল্পনা ছিল।
পা নাচছে, হাত ব্যস্ত রয়েছে, কান শুনছে— সব কিছুকে ব্যাপৃৃত করে রাখো, আর সবকে ব্যস্ত করে রাখার জন্যেই কীর্তনের এত মহিমা! আবার যদি কান কীর্তন শুনতে শুনতে অন্য কারও কথাও শোনে, সেই কথা যাতে কান না শুনতে পায় সেই জন্যে বাদ্য বাজিয়ে কীর্তন করার রীতি। শ্রীশ্রী আনন্দমূর্তিজির বাণী থেকে এমন জীবনদর্শনই পাওয়া যায়।
বড়ু চণ্ডিদাস রচিত ‘শ্রী কৃষ্ণ কীর্তন’ গ্রন্থে দেব দেবীর পূজার্চনায় কীর্তনের প্রমাণ মেলে।
শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে মোট পদের সংখ্যা ৪১৮। প্রতিটি পদে সুর, তাল ও গায়নরীতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ছন্দেরও বৈচিত্র্য রয়েছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রচনাকাল যেমন চর্যাগীতি ও লোচনদাসের ধামালি রচনার মধ্যবর্তী, তেমনি এর ছন্দরীতিও প্রাকৃত ও বাংলা-প্রাকৃত রীতির মধ্যবর্তী। সাঙ্গীতিক পরিভাষায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তন বিপ্রকীর্ণ জাতীয় গীতরূপ। দুটি গ্রাম্য গোপ বালক-বালিকার প্রণয়কাহিনী অবলম্বনে এটি রচিত। এতে গ্রামের পথঘাট, বনাঞ্চল এবং গ্রাম্যজীবনের এক স্বাভাবিক চিত্র ফুটে উঠেছে। তিনটি চরিত্র রাধা, কৃষ্ণ ও বড়াইর ছন্দোবদ্ধ উক্তি-প্রত্যুক্তির মধ্য দিয়ে কাহিনীটি বর্ণিত হয়েছে। অনেকের ধারণা, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মধ্যে বাংলার ঝুমুর গান ও লোকযাত্রার বীজ নিহিত।
শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে মোট ৩২টি রাগ-রাগিণীর উলেখ আছে। সেগুলি হলো আহের, ককু, কহু, কহু গুর্জরী, কেদার, কোড়া, কোড়া দেশাগ, গুর্জরী, দেশ বরাড়ী, দেশাগ, ধানুষী, পটমঞ্জরী, পাহাড়ী, বঙ্গাল, বঙ্গাল বরাড়ী, বরাড়ী, বসন্ত, বিভাস, বিভাস কহু, বেলাবলী, ভাটিয়ালী, ভৈরবী, মল্লার, মালব, মালবশ্রী, মাহারঠা, রামগিরি, ললিত, শৌরী, শ্রী, শ্রীরামগিরি ও সিন্ধোড়া। যেসব তালের পরিচয় পাওয়া যায় সেগুলি হলো যতি, ক্রীড়া, একতালী, লঘুশেখর, রূপক, কুড়ুক্ক ও আটতালা।
শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ব্যবহৃত ‘শৌরী’ রাগ সম্ভবত চর্যায় ব্যবহৃত ‘শবরী’ রাগের অপভ্রংশ। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ব্যবহৃত কয়েকটি রাগ-রাগিণীর পরিচয় প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্রে পাওয়া যায়, যেমন আহের (আভীর), কহু (ককুভ), রামগিরি (রামক্রি), ধানুষী (ধানশ্রী), দেশাগ প্রভৃতি।
গীতগোবিন্দম্-এ যেসব রাগ-রাগিণীর উলেখ আছে তার পরিচয় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও পাওয়া যায়। তবে গীতগোবিন্দম্-এ পটমঞ্জরী রাগে রচিত পদের সংখ্যা অধিক, আর শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে পাহাড়ী রাগে রচিত পদের সংখ্যা অধিক, যা গীতগোবিন্দম্ -এ নেই।
গীতগোবিন্দম্ -এ যেসব তালের উলেখ আছে তার পরিচয় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও পাওয়া যায়, যেমন যতি, রূপক ও একতালি। শুধু সাঙ্গীতিক দিক দিয়ে নয়, রচনাশৈলী এবং আঙ্গিকের দিক দিয়েও উভয় কাব্যের মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষ্যণীয়। এক কথায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে জয়দেবের প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছে।
বাংলা সঙ্গীতের ক্ষেত্রে বিদ্যাপতির দান অপরিসীম। তাঁর পদাবলি মৈথিলী ভাষায় রচিত হলেও একসময় তা বাংলায় খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। বৈষ্ণব-পদাবলী তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা। তাঁর পদাবলীতে যেমন আছে ভক্তিরস, তেমনি আছে মানবিক প্রেম। পরবর্তীকালের গীতিকবিরা তাঁকেই অনুসরণ করেছেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাপতির ভক্ত ছিলেন। তিনি বিদ্যাপতির অনেক পদ সুর আরোপ করে গাইতেন। বিদ্যাপতি রচিত ‘ভরা বাদর মাহ বাদর’ পদটিতে রবীন্দ্রনাথের সুর এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে।
বৈষ্ণবপদাবলি রচনার ক্ষেত্রে বিদ্যাপতি জয়দেবের অনুসারী ছিলেন। সেজন্য বিদ্যাপতিকে ‘অভিনব জয়দেব’ বলা হতো। আবার বিদ্যাপতির এক শতাব্দী পরে বাংলার বৈষ্ণবকবি গোবিন্দ দাস বিদ্যাপতির পদাঙ্ক অনুসরণ করতেন বলে ‘দ্বিতীয় বিদ্যাপতি’ নামে খ্যাত হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ গোবিন্দ দাসেরও ভক্ত ছিলেন। গোবিন্দ দাস রচিত ‘সুন্দরী রাধে আওয়ে বনি’ পদটিতে রবীন্দ্রনাথ সুর আরোপ করে ভানুসিংহের পদাবলীতে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।
বিদ্যাপতির পদগুলি শব্দমাধুর্য ও সুরলালিত্যে অসাধারণ।
বাংলার কীর্তনীয়ারা তাঁর পদসমূহ রসকীর্তন ও পালাকীর্তনের অন্তর্ভুক্ত করে তাঁকে অমর করে রেখেছেন।
সামগ্রিকভাবে বাংলার ধর্ম, সমাজ, সংস্কার ও মননে বৈষ্ণবপদাবলির প্রভাব অপরিসীম। এর প্রভাবে বাঙালীর মানবতাবোধ উজ্জীবিত হয়েছে। বৈষ্ণব মতবাদের প্রভাবে সহজিয়া ও বাউল মতবাদ পরিপুষ্ট হয়। বৈষ্ণবরাই বাংলা গীতিকবিতা রচনা এবং অলঙ্কার ও দর্শনশাস্ত্রের আলোচনার সূত্রপাত করেছেন।
প্রেমানুভূতি এবং ভাবের সূক্ষ্ম ও বিচিত্র অভিব্যক্তির কারণে বৈষ্ণবপদাবলী বিশ্বসাহিত্যের মর্যাদা লাভ করেছে।
রাধা-কৃষ্ণের প্রণয়লীলাকে অবলম্বন করেই বৈষ্ণবপদাবলির উদ্ভব। এর শুরু প্রাকচৈতন্য যুগে। চৈতন্যদেবের অনুপ্রেরণায় অসংখ্য বৈষ্ণবকবি রাধা-কৃষ্ণের প্রণয়ভিত্তিক পদ রচনা করেন এবং তা সারা বাংলায় জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।
এই পদগুলি ‘কীর্তন’ নামে খ্যাত। বাংলা সঙ্গীতজগতের এক অমূল্য সম্পদ এই কীর্তন গান। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়: ‘কীর্তনে আমরা যে আনন্দ পাই সেতো অবিমিশ্র সঙ্গীতের আনন্দ নয়, তার সঙ্গে কাব্যরসের আনন্দ একাত্ম হয়ে মিলিত।’
চৈতন্যোত্তর যুগে বাংলা ও ব্রজবুলিতে প্রায় দশ হাজারের মতো পদ রচিত হয়েছে। বৈষ্ণবপদাবলির শ্রেষ্ঠ পদকার হলেন বিদ্যাপতি, চন্ডীদাস, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, মালাধর বসু, শেখ ফয়জুল্লাহ, সৈয়দ সুলতান, বলরাম দাস, লোচন দাস, বাসুদেব ঘোষ, মুরারি গুপ্ত, নরহরি দাস, নরোত্তম দাস প্রমুখ।
বঙ্গদেশে প্রাচীনকাল থেকেই কীর্তন বা ঈশ্বরের নামগান করার প্রচলন ছিল। বৌদ্ধরাও চর্যাগান করত, যা কীর্তন গানেরই অনুরূপ। ঈশ্বরের নাম, লীলা ও গুণের উচ্চভাষণই কীর্তন। এই কীর্তনের বিশিষ্ট রূপ দেন চৈতন্যদেব। তিনি কীর্তনকে দুটি পদ্ধতিতে ভাগ করেন নাম-সংকীর্তন ও রসকীর্তন বা লীলাকীর্তন।
কীর্তনের পাঁচটি অঙ্গ কথা, দোঁহা, আখর, তুক্ ও ছুট্।
কীর্তনের অপর একটি অঙ্গ হলো ঝুমুর। বাংলা লোকসঙ্গীত এবং আধুনিক গানে ঝুমুরের প্রভাব লক্ষ করা যায়।
কাজী নজরুল ইসলাম ঝুমুর সুর ব্যবহার করেছেন তাঁর বিভিন্ন গানে, যেমন –
‘চুড়ির তালে নুরির মালা’, ‘তেপান্তরের মাঠে বঁধু হে’, ‘রাঙামাটির পথেলো’ প্রভৃতি।
কীর্তন উদ্গ্রাহ, মেলাপক, ধ্রুব ও আভোগ অনুসারে রচিত, অর্থাৎ আধুনিক কালের সাঙ্গীতিক পরিভাষায় স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ এই চার কলিতে নিবদ্ধ। কীর্তনে যেসব তালের পরিচয় পাওয়া যায়, প্রাচীন সঙ্গীতগ্রন্থে তার উলেখ আছে।
তালগুলি দক্ষিণী সঙ্গীত এবং বাংলা কীর্তনে এখনও প্রচলিত। তালগুলি হচ্ছে ধ্রুবতাল, শ্রুতিতাল, রুদ্রতাল, বৃক্ষতাল, জপতাল প্রভৃতি।
জয়দেবের গীতগোবিন্দম্ল -এর তাল এবং পরবর্তী কীর্তনের তাল প্রায় একই।
বাংলা সঙ্গীতে কীর্তনের প্রভাব অপরিসীম।
ষোলো শতকের শেষদিকে কীর্তন গান সারা বাংলায় বিস্তার লাভ করে। এ সময় কীর্তনের চারটি শাখা গড়ে ওঠে গরাণহাটি, মনোহরশাহী, রেনেটী ও মন্দারিণী। এগুলির মধ্যে মনোহরশাহী কীর্তনের প্রভাব ছিল সর্বাধিক। আঠারো-ঊনবিংশ শতাব্দীতে সমগ্র বাংলায় প্রধানত এই কীর্তনই প্রচলিত ছিল। কবিগান ও আধুনিক পাঁচালিতেও মনোহরশাহী কীর্তনের প্রভাব পড়েছে।
কীর্তন ভেঙে বাংলায় ঢপকীর্তনের সৃষ্টি হয়। মুর্শিদাবাদের রূপচাঁদ অধিকারী (১৭২২-১৭৯২) ও বনগ্রামের (যশোর) মধুসূদন কিন্নর (মধুকান) রচিত ঢপকীর্তন এক সময় অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। আখরবিহীন এই ঢপে পাঁচালি ও যাত্রাগানের প্রভাব সুস্পষ্ট। ঢপকীর্তনে সাধারণত তিন, চার, পাঁচ ও সাত মাত্রার তাল ব্যবহৃত হয়। শাস্ত্রীয় উচ্চাঙ্গ কীর্তনের মতো দশকোষী, আড়, লোফা প্রভৃতি জটিল তালের ব্যবহার এতে নেই। রবীন্দ্রনাথের বেশ কিছু কীর্তন-অঙ্গের গানে ঢপকীর্তনের ভাব ও রীতির অনুসরণ দেখা যায়।
‘ওকে বলো সখী বলো, কেন মিছে করে ছলো’ মায়ার খেলার এই গানে মধুকানের স্পষ্ট প্রভাব রয়েছে।
মধুকান রাধা-কৃষ্ণলীলা অবলম্বনে বহু পদ রচনা করেন এবং সেগুলি রাগ-রাগিণী সহযোগে গাওয়া হতো কীর্তনের মতো করেই।