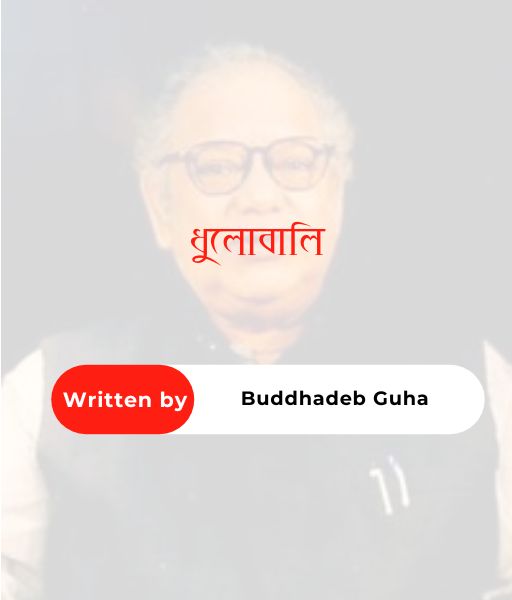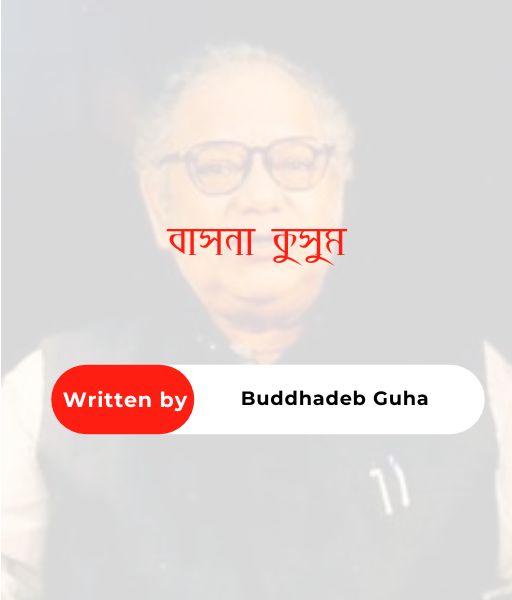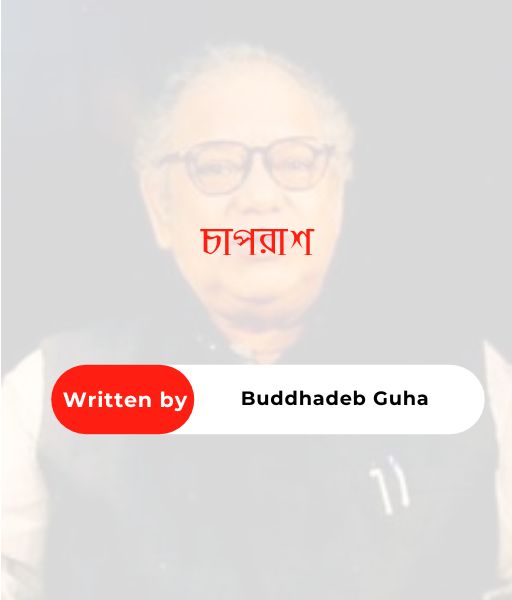রাঁধলা কী
রাঁধলা কী? ও বুড়ি?
শিলি বলল।
ফোকলা দাঁতে হাসি ফুটল কিরণশশীর।
–এখনও কিসু রাঁধি নাই। রাঁধবোনে। বুড়ির আবার রাঁধারাধির কী। দুইডা ভাত ফুটাইয়া লমুআনে। একটুক ঘি ফ্যালাইয়া, দুইডা আলু দিয়া দিমু ভাতে। আর কাঁচা মরিচ তো আছেই।
রোজ রোজ এতদেরি কইর্যা রান্ধো ক্যান। শরীলডা এক্কেরেই যাইব। তখন দেখবনে কে!
ক্যান? তুই-ই দেখবি। দেখবি না?
চুপ করে রইল শিলি। উত্তর দিল না।
–কীরে ছেমড়ি! কথা কস না ক্যান?
–কী কমু? কেডা কারে দ্যাহে? শরীল ভাইঙ্গা গ্যালে কেউই দেখব না কইয়া দিলাম।
–হে তো জানি। কিন্তু এ পোড়াকপাইল্যা শরীল একটাদিনের লগেও কি খারাপ হয়? পাথর দিয়্যা গইড়া থুইছিল আমারে ব্রহ্মা।
হাসল শিলি।
কিরণশশীর গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে, শিলি হেসে বলল, বালাই-ষাট। খারাপ হইয়া কাম নাই। এই কইরাই য্যান পার হইয়া যাও বুড়ি।
–কইছস ঠিক ছেমড়ি। দেহিস তুই। আমি পড়ম আর মরুম।
–তা, তিনি আইতাছেন কবে?
শিলি ভুরু তুলে জিজ্ঞেস করল।
–এহনে বুঝছি। তাই ক! তর এত ঘন ঘন আসন-যাওন আমার ছাওয়ালের লইগ্যাই! কীরে? ভুল কইছি? ক?
বাড়ির চারপাশ থেকে নানারকম পাখি ডাকছিল। বড়ো বাঁশঝাড়ের মধ্যে বাদামি বড়োপাখিটা ধরে ধরে পোকা খাচ্ছিল। সকালের হাওয়াতে বাঁশে বাঁশে কটকট আওয়াজ হচ্ছিল। পাশের ডোবাতে, শাপলা যেখানে ঢেকে রাখেনি জল; সেখান থেকে সাতসকালের নরম সূর্যের আলো প্রতিসরিত হয়ে এসে, তেঁতুলগাছের পাতায় পড়ে, চারদিকে আলোর চিরুনির মতন তিরতির করে কাঁপছিল।
কিরণশশী, শেষচৈত্রর প্রথম সকালের রোদে, বড়োঘরের মাটির দাওয়াতে দু-টি পা ছড়িয়ে দিয়ে বসেছিলেন।
তুমি একটা যাচ্ছেতাই। বুড়ি।
–তা তো কইবিই। আমারে ভালো কইর্যা স্যাবা-যত্ন কর। পুতন আইলে অইব কী? ছাওয়াল আমার বড্ডই মাতৃভক্ত। আমি যদি না কইরা দেই, অইবই না বিয়া। বুঝছস ছেমড়ি। আমার কথাই হইতাছে গিয়া শ্যাষকথা।
বিয়ের কথাতেই, শিলির চোখ-মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।
হাসিমুখে বলল, হঃ। কী আমার ছাওয়াল। তারে বিয়া করনের লইগ্যা আমি তো কাইন্দা বেড়াই য্যান। তুমি নিজা নিজা ছাইভস্ম ভাইব্যাই ময়রা।
-তাই তো।
হাসলেন কিরণশশীও।
বললেন, আচ্ছা। দেহি তরে কোন রাজার পুত আইয়া বিয়া করে?
শিলি ভুরু নাচিয়ে, চোখে ঝিলিক তুলে বলল, হ। হ। দেইখ্যো অনে। আমারে তুমি ভাবতাছেটা কী? তোমার ছাওয়ালরে বিয়া কেডা করে?
–যা ভাবতাছি, ঠিক-ই ভাবতাছি।
একটু পরে শিলি বলল, দাও দেহি, তোমার চাউলডা ধুইয়া আনি ইন্দারা থিক্যা।
–লইয়া যা। কুলায় যাইর কইরা থুইছি। হবিষ্য-ঘরেই রাইখ্যা আইছি।
শিলি চলে গেল হবিষ্য-ঘরের দিকে।
কিরণশশী, চলে-যাওয়া শিলির দিকে চেয়ে একটা বড়ো দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।
বড়োভালো এই মেয়েটা। রায়দের বাড়ির ছোটোতরফের ছোটোছেলের মেয়ে। ছোটোতরফের রায়রা কোনোরকমে টিমটিম করে বেঁচে আছেন এখনও। পয়সা কোনোদিনও ছিল না। বংশ পরিচয় ছিল। মানুষ ওঁরা ভালো। ভালো বলেও বটে এবং কুঁড়ে বলেও বটে; টাকা-পয়সার দিকে কোনোদিনও বিশেষ লোভ ছিল না। ঘরবাড়ি ছেড়ে উত্তরবঙ্গ থেকে উদবাস্তু হয়ে ওরা সকলেই নিম্ন-আসামের এই কুমারগঞ্জে এসে একটু মাথা গোঁজার ঠাঁই করে নিয়েছেন। তাও চল্লিশ বছর হতে চলল।
এঁদের কারও দেশ ছিল বগুড়া, কারও নিলফামারি, গাইবান্ধা, ডিমলা, কারও পাবনা বা রাজশাহি। কিরণশশীদের দেশ ছিল বগুড়ায়। এখনও পেছনে তাকালে, ফেলে-আসা দিনগুলোর কথা মনে পড়ে। মনে হয়, এই তো সেদিনের কথা। মনে পড়লেই মন খারাপ হয়ে যায়। এখনও কেন যে, মনে পড়ে! চেনাজানা মানুষজন আর নেই। অল্পবয়েসিরা চেনে না।
পুরানা পাড়া আর চেনন যায় না। বাড়িটার মধ্য দিয়া চওড়া পিচের রাস্তা চইল্যা গেছে। গিয়া। ঐশ্বনে নাকি এয়ারপোর্ট হইবে শুইন্যা আইছে হেরম্ববাবুর ছোটোপোলায়। স্যা গতবছর পূজায় গেছিল, বগুড়ায়। অনেক কথাই কইল। সেই তাগো হরিসভার পূজাও আর হয় না। মস্ত মসজিদ উঠছে। ইদের সময়ে উট বলি হয়। কোন শ্যাখেরা নাকি পাঠায় সেসব। মকবুল মিয়া, যে নাকি ঘরামির কাজ কইর্যা খাইত, এহনে মস্ত বড়লোক হইছে। ঢাউস গাড়ি চড়ে।
ভরসার কথা এই যে, পিছনের কথা মনে করার সময় তাঁর নেই-ই। হইলে হইছে। বদলাইয়া ত যাইবই। কুমারগঞ্জও কি আর সেই আগের কুমারগঞ্জ আছে নাকি। সব-ই বদলাইয়া গেছে। বদলাইয়া গেছে মানুষের মন, মানুষের দৃষ্টি, সবকিছুই এই কয় বছরে বদলাইয়া গেছে। বড়ো মানুষ। বড়ো ধুলা। বড়ো আওয়াজ। বড় খাই খাই, নোংরামি, চাইরধারে। এরমধ্যে কিরণশশীর আর বেশিদিন বাঁচার ইচ্ছা নাই। এহনে, মানে মানে যাইতে পারলেই হয়–
ভাবেন তিনি।
টিনের ছাদে বইস্যা একটা দাঁড়কাক ডাকতাছিল। লালরঙা। মাইয়াগো অসভ্য জায়গার মতন লাল তার মুখের ভিতরখান। অসভ্য-অসভ্য দেখায়।
কুমারগঞ্জের সকলেই বলে, কিরণশশী বড়োই অভাগী। দেশ ছেড়ে আসার পর আসামের এই গোয়ালপাড়া জেলার ধুবড়ি, গৌরীপুর, কুমারগঞ্জ, তামাহাট, গোয়ালপাড়া, ডিঙ্গডিঙ্গা, গোলোকগঞ্জ, ফকিরাগ্রামে অনেকেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন।
অনেকেই অবশ্য, যেমন কিরণশশীর শ্বশুরমশাই; চাষ-বাস, পাটের কারবারের কারণে এখানে অনেক আগে থেকেই ছিলেন। পাশ দিয়ে বয়ে গেছে গঙ্গাধর নদী। তার মাথা গিয়ে পড়েছে ব্রহ্মপুত্রে আর ল্যাজ রয়েছে তিস্তায়। দেশ ভাগ হবার আগে পুববাংলা থেকে বড়ো বড়ো মহাজনি নৌকো করে পাট আসত এই নদী বেয়ে। পাটের বড়ো বড়ো আড়ত, গদিঘর, সব ছিল তখন প্রত্যেক বর্ধিষ্ণু বাড়িতেই। লাল আর সাদা, মিহি আর মোটা, নানারকম পাটের গন্ধে, শীতকালে পাট ওঠার পর, পুরো এলাকাটা ম ম করত যেন। গেছে সেসব দিন।
অনেক ভেসে আসা পরিচিত পরিবার-ই এসে এখানে আবার নতুন করে শিকড় গেড়েছেন। ব্যাবসা, চাকরি ইত্যাদিতে কোচবিহার, শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, মালদা, বালুরঘাট, বহরমপুর, কৃষ্ণনগর এবং কলকাতাতে অনেকে ছড়িয়ে গেছেন। যদিও আগে আসা বা পরে আসা সকলের-মূল এখনও রয়ে গেছে এই ধুবড়ি, গৌরীপুর, কুমারগঞ্জ, তামাহাটেই।
সাত-সাতটি সুন্দর, কৃতী যুবক ছেলেকে এবং তাঁর স্বামীকেও হারিয়েছেন কিরণশশী। আছে এখন এই সবেধন পুতন, সবচেয়ে ছোটোছেলে। পুতনের সঙ্গে তাঁর বয়সের এতই তফাত যে, মনে হয় তিনি বুঝি মা নন, পুতনের ঠাকুমা।
পুতন, জলপাইগুড়ির এক চা-বাগানের অ্যাকাউন্ট্যান্ট। ধুবড়ি থেকে বি.কম. পাশ করে কলকাতায় গেছিল তাঁর ভাসুরের ভগ্নীপতির অডিট-অফিসে খাতা লেখার কাজ শিখতে। এম-কমও পাশ করে সেখান থেকেই। তারপর তাঁদের-ই সুপারিশে, তাঁদের মক্কেলের এই চা-বাগানে অ্যাকাউন্ট্যান্ট হয়ে যোগ দিয়েছে বছর তিনেক হল।
পুতনের কাছেই শুনেছিলেন কিরণশশী যে, একসময়ে বেশিরভাগ নামি চা-বাগান-ই ছিল বাঙালিদের। নয়তো সাহেবদের কোম্পানির। এখন সাহেবদের কোম্পানিগুলো কিনেছে বড়ো বড়ো মাড়োয়ারিরা আর বাঙালিদেরগুলো তাদের চেয়ে ছোটো মাড়োয়ারিরা। হাতে বাঙালিদের মাত্র কয়েকটি বাগান-ই আছে এখন। হাতে গোনা যায়।
পুতন, বছরে একবার করে আসে কুমারগঞ্জে, একমাসের জন্যে। এবার আসবে বৈশাখের প্রথমে। চিঠি লিখেছিল যে, এবারে নববর্ষটা কুমারগঞ্জেই কাটাবে। আর সাত বোশেখির মেলা দেখতে যাবে অনেকদিন পর, আলোকঝারি পাহাড়ে।
শিলি এসে বলল, তোমার ভাত চড়াইয়া দিয়া আইলাম। একটু মটরের ডাইলও ধুইয়া ছড়াইয়া দিছি। দুইডা আলু আর দুই টুকরা কুমড়া। সময়মতো নামাইয়া লইও অনে। আমি যামু?
–আইসাই যামু যামু করস ক্যান রে ছেমড়ি? ঘোড়ায় জিন দিয়া আইছস নাকি?
–হেইরকম-ই পেরায়। বাবার যে, জ্বর হইছে, তাই-ই বুঝি কয় নাই তোমারে?
–কে?
হোন্দলের মায়ে?
না তো! হোন্দলের মায়ের কথা ছাড়ান দে। আয়, আর যায়। যার ঘরে চাইর-চাইরটা পোলাপান, হেই মায়ে কি কোথাওই মন লাগাইয়া কাম কইরবার পারে? ক দেহি? ক্ষুধায় কান্দে সেগুলান। আর তার ভাতার তো দিনরাত মদ গিল্যা পইড়াই থাহে। হে বেচারিই বা করেডা কী?
-তুমিও তো একলা বুড়ি মানষি। তোমারে যদি নাই-ই দ্যাহে, তো ছাড়াইয়া দ্যাও না ক্যান? তোমারে দ্যাহে কেডায়?
–থাক। থাক। অমন কথা কইস না। ছাড়াইয়া দিলে, পোলাপানগুলানরে লইয়া এক্কেরে না-খাইয়া মরব।
–পোলাপান হয় ক্যান তাগো? যাগো খাওয়াইবার
–স্যা হোন্দলের মায়ের কী দোষ। পোলাপান হয় ক্যান তা জিগাইবার লাগে হোন্দলের বাপরে। এই পুরুষ জাতটার হক্কল-ই এক্কেরে বেআক্কাইল্যা।
শিলি আর কথা বাড়াল । ও ভুলেই গেছিল যে, পুতন কিরণশশীর নিজের আট নম্বর এবং শেষছেলে। মধ্যে তিনটি মেয়েও ছিল। দু-টি মারা গেছে কৈশোরে। একটির বিয়ে হয়েছে কোচবিহারে। তার স্বামী রেলের টিকিট কালেক্টর।
খুব সময়মতো মনে পড়ে যাওয়ায় চুপ করে গেল ও।
পুরুষমানুষগুলোর সত্যিই কি কোনো আক্কেল ছিল না? ছিল না শুধু নয়, এখনও নেই। নইলে হোন্দলের বাবায় এমনডা করে। ছিঃ ছিঃ।
–চলি বুড়ি।
–আরে। তর বাবার না জ্বর আইছে কইলি, তা এহনে বাবা আছে ক্যামন, তা তো কইয়া গেলি না রে ছেমড়ি। কী যে করস।
–ভালো নাই। জ্বর উইঠ্যা গেছিল পাঁচ। এখন নাইম্যা দুই হইছে।
–ঔষধ-টোষধ দিছস কিছু? না, ভালোবাসাতেই ছাইড়া যাইব গিয়া জ্বর?
–দিছি তো! শৈলেন ডাক্তারের ভাইরে আনাইছিলাম তামাহাট থিক্যা। কইয়া গ্যালেন, মাথার নীচায় কচুপাতা দিয়া কইষ্যা জল ঢাইল্যা যাও আর কুইনিন মিক্সচার চালাইয়া যাও!
-হইছেডা কী? ম্যালোরি নাকি? তাইলেই খাইছে।
–আঃ। বুড়ি, তোমারে লইয়া পারি না আর। তোমার ছাওয়াল হইল গিয়া ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির ফার্স্ট ক্লাস এম. কম, আর তুমি ম্যালেরিয়ারে কও ম্যালোরি? এক্কেরে হোন্দলের মা হইয়া গ্যালা দেহি।
-ওই হইল। বুঝছস তো তুই। বোঝন যাইলেই হইব। ইংলিশ-ফিংলিশ আমি জানুম কোঙ্কিা এত? দেহি, আজ বিকাল বিকাল যাইয়া একবার দেইখ্যা আসুমনে নরেশরে।
-তোমারে কে দ্যাহে তার ঠিক নাই। তোমার কাম নাই যাওনের। তেমন যদি বুঝি তো, আমিই পাঠামু অনে ক্যাবলারে। তোমারে বইল্যা যাইব আইস্যা। খামোকা আইস্যা ভিড় বাড়াইও না তো!
-আমি তো ভিড়-ই বাড়াই শুদামুদা। এহন আর কোন কামে লাগি কার?
অভিমানের সুর লাগল গলায়, কিরণশশীর।
তারপর বললেন, তর কাকায় বাড়ি নাই বুঝি? ঘরে পুরুষমানুষ নাই একজনও?
-নাঃ। শিকারে গেছে গিয়া আবু ছাত্তাররে লইয়া। ধুবড়ি থিক্যা কোন সাহেব আইছে নাহি শুনি।
–পুরুষমানুষ লইয়া, কোন কাম আমাগো। বেকামের লোক সব। কামের মধ্যে এক কাম। সে কাম ত কুত্তায়ও করে। বাহাদুরিটা কীসের অত?
সবসময় শিকার-শিকার। কী যে, বাতিক হইছে পরেশের। কাম-ধান্দা নাই। ঘরে একটা কচি মাইয়ারে ফ্যালাইয়া।
একটু চুপ করে থেকে আবার বললেন কিরণশশী, তর বাবার জ্বর দেইখ্যা যায় নাই নিশ্চয়? পরেশ?
-না তো কী! যখন চইল্যা গেল, তখন বাবায় তো বেহুঁশ।
–কস কী তুই? কী খিটক্যাল। এমন বেআক্কাইল্যাও হয়। ক তো দেহি।
–চলি আমি এহনে।
–যাওন নাই। আইসো।
তারপর গলা তুলে বললেন, আবার আসিস লো ছেমড়ি।
শিলি শুনতে পেল কি না বুঝতে পারলেন না উনি।
না শুনে থাকলে না শুনুক। ওঁর বলার, উনি বললেন।
চ্যাগারের দরজা পেরিয়ে রক্তজবা গাছটার পাশ দিয়ে জোড়া-রঙ্গনের পাশ কাটিয়ে, পেছনের বাঁশবনের মাঝের আলোছায়ার ডোরাকাটা পথে পুকুর থেকে সদ্য উঠে বাড়ির দিকে ফেরা হেলতে-দুলতে আসা, হিস-হিসানি তোলা, একপাল সাদা কালো বাদামি হাঁসেদের মধ্যে দিয়ে, তাদের দু-ভাগ করে নিয়ে; সাদা-কালো ডুরে-শাড়ি জড়ানো কালো ব্লাউজ-পরা শিলি; আলো-ছায়ার-ই মতো মিলিয়ে যাচ্ছে। ওর ডান বগলের কাছে ব্লাউজটা ছিঁড়ে গেছে একটু। নবীন যুবতীর সুগন্ধি ঘামে ভিজে গেছে বগলতলি। এ বাড়িতে কোনো পুরুষ নেই বলে, আঁচল দিয়ে ঢাকেনি শিলি, বগলতলি। পুরুষগুলোর চোখ দুপুরের কাকের মতন। কিরণশশী মুগ্ধ, স্নেহময় দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন ওর পথের দিকে, অনেকক্ষণ।
রঙ্গনের ডালে বুলবুলি হুটোপাটি করছিল। মৌটুসি পাখি ডাকছিল জবা আর যজ্ঞিডুমুরের পাতার আড়ালের ছায়া থেকে, প্রথম গ্রীষ্মের রোদের আঁচ বাঁচিয়ে। বাঁশবাগান থেকে ঘুরঘুর রঘু-ঘুঘুর-র-র-ঘুউ করে কচি দুপুরের বিষণ্ণতাকে ছিদ্রিত করছিল একজোড়া ঘুঘু। দমক দমক হাওয়ার, ধমকে ধমকে হলুদ ও লাল শুকনো কাঁঠাল-পাতারা ঝাঁট দিচ্ছিল উঠোন, বিনামাইনের মর্জিবাজ মুনিষের মতন, থমকে থমকে।
নেশা লেগে গেল কিরণশশীর। শেষচৈত্রর চড়া বেলায়ও চোখের দৃষ্টি যেন ঝাপসা হয়ে এল হঠাৎ-ই, শিলির চলে যাওয়া পথের দিকে চেয়ে। শোক এবং স্বপ্ন দুই-ই বোধ হয় চোখের দৃষ্টিকে সমান ঝাপসা করে।
ভাবলেন উনি। বয়স হলে, সঙ্গীহারা হলে বড়ো ঘন ঘন ঝাপসা হয় চোখ। কিরণশশী, বড়োঘরের দাওয়া থেকে উঠে চান করতে গেলেন বাথরুমে। ইন্দারার একপাশে কিছুটা জায়গা বাঁধানো এবং ঘেরা। দরজা-দেওয়া। মেয়েদের চান করার জন্যেই বানিয়েছিলেন গোপেনবাবু। যখন বেঁচেছিলেন।
তাও অনেকদিনের কথা হয়ে গেল।
চান করতে করতে কিরণশশী নিজেকে দেখেন আর বড়োকষ্ট হয় তাঁর। সুন্দরী নারীর যৌবন চলে যাওয়ার সময়ে অনেক কিছুই সঙ্গে টান মেরে উপড়ে তুলে নিয়ে যায়। আর যৌবন যখন থাকে, সে মদমত্ত উদ্ধত থাকে বলে, কোনো সুন্দরী যুবতীই দুঃস্বপ্নেও ভাবে না, একমুহূর্তের জন্যেও যে, যৌবন বড়ো অল্পসময়ের জন্য আসে, থাকে; চাঁপার বনের গন্ধের মতন। তারপর সেই শূন্যগহ্বর, সুখ-স্মৃতির গূঢ় গভীর গোপন সব অস্পষ্ট ছায়া বুকে বেঁচে থাকে। দেওয়াল থেকে, অনেকদিন ধরে টাঙিয়ে রাখা ছবি বা ক্যালেণ্ডার হঠাৎ সরিয়ে নিলে যেমন চারদিকের অনুষঙ্গের মধ্যে সেই জায়গাটি বড়োই দৃষ্টিকটু লাগে; সুন্দরী নারীর বার্ধক্যও তেমন-ই। সহজে, সুখে বইতে পারা কঠিন।
এই চান করার সময়টাতে প্রত্যেকদিন-ই নিজেকে অভিশাপ দেন কিরণশশী। তাঁর এই একলা জীবনে আর কোনো মোহ নেই। আশা নেই। ভালোলাগা নেই। বেঁচে আছেন, রান্না করছেন, ভাত খাচ্ছেন, ঘরবাড়ি পরিষ্কার করে রাখছেন, শুধু একটিমাত্র স্বপ্ন বুকে নিয়ে। পুতনের সঙ্গে শিলির দুটি হাত মিলিয়ে দিতে পারলেই তাঁর বেঁচে থাকার সব প্রয়োজন-ই ফুরিয়ে যাবে। একদিন এই পলেস্তারা খসে-যাওয়া ইন্দারার পাশের করমচা-রঙা চানঘরে তাঁর একমাত্র বেঁচে থাকা ছেলের বউ, সুন্দরী যুবতী শিলি চান করবে।
নিজে চান করতে করতে ভাবেন, কিরণশশী। সুগন্ধি সাবান আর তেলের গন্ধে ঢেকে যাবে এই করমচা-রঙা মেঝের ক্ষারের গন্ধভরা চানঘরখানি।
তাঁর পোলার বউ। রাতভর বরের সোহাগ খেয়ে, নতুন সিঁদুর-লেপটানো কপাল আর লাল নাক নিয়ে, ব্ৰীড়ান সোহাগি বেড়ালের মতন আড়ামোড়া ভেঙে, যখন পরিচিত অথচ একেবারে নতুন শিলি; গড়ানো সকালের চৌকাঠে এসে দাঁড়াবে প্রথম সোহাগের পরের চান করার জন্যে, তখন চান করতে করতে হাই তুলবে শিলি। সিঁদুরে-আমের ডালে-বসা বসন্ত বৌরি পাখি লোভীর মতো দেখবে সেই ছাদখোলা চানঘরের মধ্যের শিলির জলভেজা নগ্ন রূপ। তারপর কচিপাতা-ভরা চিকন ডালে শিহর তুলে আমের বোলের গন্ধ চাড়িয়ে দিয়ে উড়ে যাবে, তার সখার কাছে।
হলুদপাখিরা হলুদ ভাষায় কথা বলে। গিয়ে বলবে, আদর করো। আদর করো। আমার খুব আদর খেতে ইচ্ছে করছে গো।
তার হলুদ সখা তাকে বলবে, অনেক কাজ। সময় নেই, সময় নষ্ট করবার।
পুরুষগুলো পৃথিবীময়-ই সব একরকম। সে পাখিই হোক। কী মানুষ! মেয়েদের মনের কথা কেউই বোঝে না। ওদের সময় হলে, ইচ্ছে হলেই ওরা আদর করতে চায়। তখন না বললেই, ভারি গোসসা।
বেআক্কাইল্যা, এক্কেরেই বেআক্কাইল্যা এই পুরুষগুলান।
ভাবছিলেন নিজের মনেই, কিরণশশী।
কে জানে? পুতন, শিলির মতো মেয়ের যথার্থ দাম দেবে কি না! শিলিদের অবস্থা পড়ে না গেলে, শিলির মতো মেয়েকে বউ করার স্বপ্নও দেখতে পারতেন না কখনো কিরণশশী।
.
জ্বরটা দুপুরের দিকে বাড়ে, বিকেলে ছেড়ে যায়। আবার বেশি রাতে আসে।
শৈলেন ডাক্তারের ভাই, দাদা ডাক্তার এই সুবাদেই গাঁয়ের ডাক্তার। এল-এম-এফ-এর ডিগ্রিও নেই। কোয়াক।
ভাইয়ের ভিজিট দু-টাকা আর দাদার আটটাকা। ভাই সামলাতে না পারলে দাদাকে ডাকে। তবে নরেশবাবুর বাড়াবাড়ি হলেও শৈলেন ডাক্তারকে আটটাকা ভিজিট দিয়ে ডাকার সামর্থ্য শিলির নেই। রোজগেরে বলতে তার কাকা পরেশ একাই। কিন্তু শিকারের বাতিকেই তাকে খেল। মানুষটা ভালো। বিয়ে-থাও করেনি। জঙ্গল-ই তাকে পরির মতো জাদু করেছে। তার বিয়ে হয়েছে জঙ্গলের সঙ্গেই।
কী যে, ঘুরে বেড়ায় সারাবছর বনে-পাহাড়ে, নদী-নালায়, তা সেই জানে। আর সঙ্গী হয়েছে বটে একজন। আবু ছাত্তার। তার বাবাকেও বাঘে খেয়েছে। তাকেও দু-বার চিতাবাঘে ঠ্যাং কামড়ে আর ঘেঁটি কামড়ে ঘা করে দিয়েছিল। হাসপাতালে ছিল একবার দু-মাস, একবার তিনমাস। তাতেও কি মতিগতি কিছু বদলাল? না। কিছুমাত্রই না।
কিন্তু নরেশের ভাই পরেশ, সে মানুষ নয়, ডাকাত। ভদ্রলোকের বাড়ির ছেলে যে, কী করে এমন হয় গেল, কে জানে। ওর সর্বনাশ করেছে আসলে ওই চালচুলোহীন, মাথার ওপরে পঞ্চাশটা মামলা-ঝোলা আবু ছাত্তার। ওটা মানুষ নয়-ই! ওদের দোজখ-এর কোনো জীব-ই হবে।
আবু ছাত্তারের দুটি চোয়ালের দিকে তাকালেই শিলিরও ভয় করে খুব-ই। অথচ ছোটোখাটো মানুষটি। মুখে হাসি লেগেই আছে।
মানুষের মুখের ভাবে পুরো মানুষ হয়তো কখনোই থাকে না, থাকে তার এক ফালি মাত্র। ইদের চাঁদের মতো। কখন যে-তাদের অমাবস্যা আর কখন পূর্ণিমা, তা বোধ হয় এমন মানুষেরা নিজেরাও জানে না। বুঝতেও পারে না।
শৈলেন ডাক্তারের ভাই জ্বরের হিসেব রাখতে বলে গেছেন। ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে হিকস-এর থার্মোমিটারের পারা নামিয়ে বাবার বগলতলায় দেয় শিলি। বার বার। ঘড়ি ধরে।
মা চলে গেছেন পাঁচবছর হল। তারপর থেকে বাবার দেখাশোনা সব শিলিই করে। ক্যাবলাই বাড়িতে একমাত্র কাজের লোক। বেশি কাজ থাকলে, মুনিষ ভাড়া করে নেয়। চালের খড় নিড়িয়ে নতুন করে ছাইতে, ঘরামিকে ডেকে নেয়।
জ্বরটা দেখে, স্নান করতে যাবে ও। বাবাকে বার্লি খাওয়াবে ফিরে এসে। নীল রঙের পিউরিটি বার্লির কৌটোটায় বেশি আর নেই। আনতে দিতে হবে ক্যাবলাকে একটা। মধুর দোকান থেকে। সে যখন ছোটো ছিল, মা তাকেই পাঠাতেন মুদির দোকানে। যেখানে সেখানে। মেয়েরা বড় হলেই তাদের জগৎ সঙ্গে সঙ্গে ছোটো হয়ে যায়।
গঙ্গাধর নদী বয়ে গেছে বাড়ির পেছন দিয়ে। ছটো যখন ছিল, তখন নদীতে কত ঝাঁপাঝাঁপি করেছে বন্ধুদের সঙ্গে। তখন সমবয়সি ছেলেরাও বন্ধু ছিল। ছেলে আর মেয়েরা যে, আলাদা জাত, তা তখন অত বোঝেনি। উদবেড়ালের গর্ত ছিল নদীর উঁচু বালির পাড়ে। শুশুক ভেসে উঠত মাঝে মাঝেই। এই গঙ্গাধর-ই গিয়ে মিলেছে তিস্তাতে। একবার কাকার সঙ্গে শীতকালে গেছিল নৌকো চড়ে, তিস্তা পর্যন্ত। হাঁস মারতে গেছিল কাকা, মনা জেঠুর সঙ্গে। তামাহাটের মিত্তিরদের বাড়িতে এসে উঠতেন মনা জেঠু।
কী সুন্দর স্বচ্ছ জল গঙ্গাধরের। তিস্তার কাছাকাছি গেলে, আরও স্বচ্ছ। এতই স্বচ্ছ যে, জলের নীচে কমলা-গেরুয়ারঙা বালির ওপরের রংবেরঙের গোল গোল নুড়ি দেখা যায়। কত রং-বেরঙা হাঁস। বড়ো, ছোটো। ছাইরঙা রাজহাঁস। কোঁয়াক-কোঁয়াক-কোঁয়াক করে উড়ে যায়, মাথার উপর দিয়ে। সেবারে অনেক-ই ডিম-সেদ্ধ, পাউরুটি, আর কলকাতার কেক খেয়েছিল, মনে আছে।
দেশ ভাগ হওয়ার আগে পর্যন্ত তামাহাট খুব বড়ো বন্দর ছিল। পাট বেচাকেনা হত। পূর্বপাকিস্তানের পাট-চাষের সব জেলা থেকে বড়ো বড়ো মহাজনি নৌকো করে পাট আসত। জায়গাটা খুব-ই রমরম করত নাকি তখন। তামাহাটের জেঠিমার কাছে শুনেছে সেইসব সুখের, স্বচ্ছলতার দিনের গল্প। হাটের দিনে, গোরুর গাড়ি করে ব্রহ্মপুত্র আর তিস্তার মহাশোল মাছ আসত। মস্ত মস্ত। বড়ো বড়ো, লাল-রঙা তাদের আঁশ। পাথালি করে রাখলে, গোরুর গাড়ির শরীর ছাড়িয়ে যেত মাছগুলো। যেমন দেখতে, তেমন-ই স্বাদ।
ওরাও ছোটোবেলায় যে, কিছুমাত্র দেখেনি এমন নয়, কিছু কিছু দেখেছে। দিশি ঘোড়ায় চেপে মুসের মিয়া আসত বাঘডোরা গ্রাম থেকে হাটের দিনে। সাদা চুলের ওপরে কালো কাজকরা মুসলমানি টুপি বসান। তামাহাটের হাটের গন্ধ এখনও নাকে লেগে আছে শিলির। গুড়, চিনি, খোল, সরষের তেল, কেরোসিন তেল, পাট, ধুলো, তামাক পাতা আর গোরু মোষের গন্ধ মিলে এক আশ্চর্য মিশ্রগন্ধ উঠত হাট থেকে। সে-গন্ধ এখনও নাকে লেগে আছে। সময় চলে যায় ঠিকই, কিন্তু স্মৃতিতে সেইসব বর্ণোজ্জ্বল শব্দ-দৃশ্য-গন্ধ বড়ো অবিশ্বাস্যরকম জীবন্ত হয়ে থেকে যায়।
বারোবছর বয়সে শাড়ি ধরিয়ে ছিলেন মা। ও যখন হঠাৎ বড়ো হয়ে গেল একদিন, সেদিনের সেই ভয়, আনন্দ আর রহস্যের দিনের কথা এখনও মনে পড়ে। মা নিজের ঘরে ডেকে নিয়ে অনেক কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন, মেয়েদের অনেক-ই বিপদ। এই পৃথিবীর কোনো পুরুষমানুষকেই বিশ্বাস না করতে বলেছিলেন। কাউকেই । এক নিজের বর ছাড়া, যখন বিয়ে হবে।
শিলি জিজ্ঞেস করেছিল, বাবাকে?
-না। বাবাকে, কাকাকে, কাউকেই না।
বড়ো ভয় করেছিল শিলির। এ কেমন বড়ো-হওয়া যে, বাবাকেও পর করে দেয়? সুন্দর এক আশ্চর্য রস-গন্ধ-স্বাদে ভরা পৃথিবী ছিল তার। বাঁশবাগানের আলোছায়ার খেলা ছিল। নদীতে সাঁতার কাটা ছিল, আকাশ পরিষ্কার থাকলে, যখন ভুটানের পাহাড় দেখা যেত উত্তরের আকাশে; হিমালয়, কখনো-কখনো কাঞ্চনজঙ্ঘাও, সোনার মতো ঝলমল করে উঠত সেই পাহাড়শ্রেণির চুড়ো। শরতের মেঘের মধ্যে, আগুন লেগে গেছে বলে মনে হত তখন। দাঁড়িয়ে থাকত, খোলামাঠে তার খেলার সাথি কুমারের হাতে হাত রেখে। মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে।
চলে গেল সেইসব দিন। কেমন হঠাৎ। বড়ো হঠাৎ-ই চলে গেল ছেলেবেলাটুকু। বৃষ্টি মাথায় করে কদমতলায় রাধাকৃষ্ণ খেলা। তাও চলে গেল।
মেয়েদের শরীর যে, মেয়েদের এতবড়ো শত্রু, তা মোটে বারোবছর বয়েসেই জানতে পেরে, বড়োই কষ্ট হয়েছিল শিলির। মেয়ে হয়ে জন্মেছে বলে, নিজেকে অভিশাপও দিয়েছিল বার বার। আশীর্বাদও মনে হয়, মাঝে মাঝে এখন। অবিমিশ্র দুঃখ বা সুখ কোথাওই নেই, তা বুঝে।
এখন, এই ঘেরাটোপের জীবন-ই অভ্যেস হয়ে গেছে। মেনে নিয়েছে যে, মেয়েরা আলাদা সৃষ্টি বিধাতার। আলাদা জাত। ছোটোজাত। পুরুষের কৃপাধন্য তারা।
বাবার জ্বরটা লিখে রেখে দিল স্লেটে।
তারপর বাবাকে বলে চান করতে গেল, ইন্দারার পাড়ে।
ক্যাবলাটার বয়স হবে পনেরো-ষোলো। ও এই সময় থাকে না। একদিন চান করার সময় শিলি হঠাৎ-ই দেখেছিল যে, ইঁদারার পেছন দিকের মানকচুর ঝোঁপের মধ্যে লুকিয়ে, ক্যাবলা চান দেখছে শিলির। ভেজা কাপড় জড়িয়ে নিয়ে দৌড়ে গিয়ে এক থাপ্পড় মেরেছিল ওকে।
বলেছিল, চোখ গেলে দেব। বুঝেছিস!
তারপর থেকে ও ভালো হয়ে গেছে। ক্যাবলা বলেই হয়তো হয়েছে। চালাক হলে হত না।
চান করতে করতে শিলি ভাবছিল, ক্যাবলা তার চান করা দেখেছিল বলে তাকে চড় মেরেছিল ও। অথচ এমনও কেউ আছে, যাকে সবকিছুই দেখানোর জন্য সে উন্মুখ। অথচ তার-ই কোনো সাড়া নেই।
কী আশ্চর্য! কেন যে, এমন হয়!
মনে আজকাল ভয়ও হয় শিলির। পুতনের ব্যবহারে। পুতনের বয়স হবে ছাব্বিশ-সাতাশ। শিলির বাইশ। এত বয়েসি কুমারী মেয়ে এখন আর এখানে নেই। না, একজনও নয়।
বিয়ে অবশ্যই কাল-ই হতে পারে।
গদাইদের অবস্থা ভালো, আলোকঝারি পাহাড়ের নীচে অনেক ধানজমি। কাঠের ব্যাবসা। ধুবড়িতে তার বাবার কয়লার দোকানও আছে। বড়োদাদা স্টিমার কোম্পানিতে সাপ্লায়ার। ধুবড়িতে। মেজদাদা ম্যাচ ফ্যাক্টরির। গদাই, ছোটোছেলে। চাষ-বাস দেখাশোনা করে। শরীর, স্বাস্থ্য ভালোই। নাক থ্যাবড়া। গা দিয়ে একটা অদ্ভুত গন্ধ। নাদু ময়রার গায়ে যেমন ছানাছানা, চিনির শিরাশিরা গন্ধ, তেমন-ই মাটি-মাটি গন্ধ।
বর হিসেবে ওকে ভাবাই যায় না। কখনোই না। লেখাপড়াও করেছে মাত্র পাঠশালা অবধি। অথচ শিলির বাবার খুব-ই ইচ্ছে। শুধুমাত্র গদাইদের অবস্থা ভালো বলেই। গলায় কলসি বেঁধে নদীতে ডুবে মরতে ইচ্ছে করে মাঝে মাঝে শিলির। বেঁচে আছে ও শুধুই তার পুতনদার-ই আশায়, পুতনদার-ই জন্যে।
আগে, সপ্তাহে অন্তত একটি করে চিঠি লিখত পুতনদা। ফটোও পাঠিয়েছিল গতবছরে। সাইকেলে হেলান দিয়ে কালোডোরা ফুলশার্ট আর প্যান্ট পরে চা-বাগানে তার অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে আছে পুতনদা। ধবধবে রং। মুখটা গোলগাল। কিন্তু খুব মিষ্টি। কত সব খবর দিত সে তখন, প্রত্যেক চিঠিতে। বারো বছর বয়সে যে-জগৎকে হারিয়েছিল শিলি, পুতনের চিঠির মাধ্যমে সেই জগৎকেই ফিরে পেয়েছিল আবার।
পুতনকে শিলিগুড়িতেও যেতে হত মাঝে মাঝে। অন্য সব বাগানেও বকেয়া পাওনা উশুল করতে যেতে হত।
ও লিখত, আজ বাগরাকোটের সাহেব ম্যানেজার ডোনাল্ড ম্যাকেঞ্জি সাহেব আর তার বউ, বেটি ম্যাকেঞ্জিকে দেখলাম। আহা! দেখে মনে হয় যেন ইংরেজি বায়োস্কোপ দেখছি। কী সুন্দর যে, সাহেব-মেম! নিজে চোখে না দেখলে বিশ্বেস-ই হত না।
একদিন লিখল, তিস্তার চ্যাংমারীর চরে নতুন করে চাষের বন্দোবস্ত হচ্ছে। রিক্ল্যামেশন হচ্ছে চর। এই চরের ঘাস পরিষ্কার করে চাষাবাদ হবে ভবিষ্যতে। তিস্তার সব চরেই চা বাগানের ম্যানেজারেরা বাঘশিকারে যেতেন। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের হাতি, পুলিশের হাতি সব এসে নাকি জমায়েত হত। উত্তর বাংলার কমিশনার আইভ্যান সুরিটা, ডি-আই-জি রঞ্জিত গুপ্ত, চিফ সেক্রেটারি রণজিৎ রায়, শিলিগুড়ির দুর্গা রায় আরও কত সব লোকের কথা লিখত পুতনদা। লিখত, জলপাইগুড়ির রানির কথা। রানি অশ্রুমতী দেবী-রায়কতদের রানি। তাঁর একমাত্র মেয়ে, রাজকুমারী প্রতিভা দেবী। তাঁর সঙ্গে নাকি বিয়ে হয়েছিল কমিউনিস্ট নেতা জ্যোতি বসুর দাদা ডাক্তার কিরণ বসুর। জ্যোতি বসুর ডাকনাম যে, গণা, তাও পুতনদার চিঠিতেই ও তখন জানতে পারে।
জলপাইগুড়ির রাজবাড়িতে একজোড়া সাপ ছিল, বিখ্যাত। সে সাপেরা ছিল বাস্তুসাপ। কারওকে কিছু বলত না নাকি!
পুতনদা বছরখানেক হল চিঠি দেওয়া একেবারেই কমিয়ে দিয়েছে। মাসে একটা লিখত ছ মাস আগে। তারপর দু-মাসে একটা।
শেষ চিঠি পেয়েছে ছ-মাস আগে। এবারে হয়তো বছরে একটা লিখবে। তারপরে থেমে যাবে চিঠি আসা, একেবারেই।
মাসিমা কিরণশশীর কাছে শুনেছে শিলি যে, পুতনদার কুমারগঞ্জে আসার আর দেরি নেই। সঙ্গে করে নাকি বাগানের ম্যানেজারের কাছে বেড়াতে আসা ম্যানেজারের শালার ছেলেকে নিয়ে আসছে। কলকাতার ছেলে। গ্রাম নাকি দেখেনি সে আগে। তাই-ই আসছে পুতনদার সঙ্গে। ছেলেটি নাকি পুতনদার-ই সমবয়েসি, যেমন লিখেছে মাসিমাকে, পুতনদা। ভালো কাজ করে নাকি কোনো বিলিতি কোম্পানিতে। ভালো মানে, উঁচুদরের কেরানি। পুতনদা নাকি দুঃখ করে লিখেছে, ম্যানেজারের শালার ছেলে মানে, ম্যানেজার-ই। তাকে খাতির-যত্ন করে খুশি রাখতেই এবারের ছুটিটা কেটে যাবে। যদি-না সে আগেই ফিরে যেতে চায় কুমারগঞ্জ থেকে। তার চাকরিটা শখের। অঢেল পয়সা। বনেদি পরিবার।
তবে শিলিকে লেখেনি কিছুই। যা লেখার তা সব-ই মাসিমাকে লিখেছে। তাই খুব-ই অভিমান হয়েছে শিলির। ভয়ও যে হয়নি, তাও নয়। নানারকম ভয়েই বড়ো বিষণ্ণ হয়ে আছে। ও, ক-দিন হল। সবসময়ই বুক দুরদুর করে।
চা-বাগানে কি অন্য কোনো মেয়ের সঙ্গে ভাব হল পুতনদার? একটা চা-বাগানে নিশ্চয়ই অনেক বাঙালি কর্মচারী থাকেন। বিশেষ করে, বাগানের মালিক যখন বাঙালিই। তাঁদের সব বাড়িতে কি শিলির চেয়ে সবদিক দিয়ে ভালো একটি মেয়ে নেই? না থাকলেও, তাদের কত শালি-টালিরাও আসতে পারেন তো বেড়াতে। কে জানে, কী হল? কেন হঠাৎ নীরব হয়ে গেল পুতনদা?
খুব-ই রাগ হয় শিলির, সেইসব অদেখা মেয়েদের ওপরে। তাদের তো কতই আছে বাছাবাছির। শিলি যে, ইন্দারার ব্যাং। ওর যে, পুতনদা ছাড়া আর কেউই নেই এই জগতে। সেই শিশুকালের সাথি। সুখ-দুঃখের মধ্যে বেড়ে উঠেছে দু-জনে। একসঙ্গে। একই ধরনের বোঝাবুঝি, সমঝোতাও গড়ে উঠেছে দু-জনের মধ্যে।
তবে, সত্যি কথা বলতে কী, এই পুতনদা যে, তার মনের আদর্শ পুরুষ, তা আদৌ নয়। তবে, পুতনদা ছাড়া আর অন্য কোনো পুরুষের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগও তার আসেনি। বাছাবাছির সুযোগ না থাকাতে, যা হাতের কাছে থাকে, তাকেই ভালো লাগাতে হয়। দেখতে দেখতে, একসময় ভালো লেগেই যায়। বার বার মনোযোগ দিয়ে কোনো গাছের দিকে তাকালেও তাকে ভালোবেসে ফেলে মানুষ; মানুষকে তো বাসতেই পারে। বাসেই!
আদর্শ পুরুষ বলতে সে নিজে যা বোঝে তেমন মানুষের সঙ্গে তার বিয়ে কোনোদিনও হবে না। কোনো মেয়ের-ই জীবনের আদর্শ পুরুষের সঙ্গেই বিয়ে কখনোই হয় না তার, আর যা-কিছুই হোক-না-কেন। হয়তো, না হওয়াই ভালো। একঘরের মধ্যে খুব-ই কাছাকাছি থেকে, দিনের পর দিন দেখলে, সব আদর্শের-ই রং চটে যায়। জেল্লা ম্যাটম্যাট করে। আদর্শ ব্যাপারটার মধ্যেই বোধ হয় দূরত্বের আর যাত্রার গন্ধ আছে একটু। ওসব দূরে রাখাই ভালো। শিলির আদর্শ পুরুষের কাছাকাছি মাত্র একজনকেই দেখেছিল সে, তামাহাটে।
মিত্তিরদের বাড়িতে বেড়াতে এসেছিল সেই ছেলেটি, কলকাতা থেকে। মাসখানেকের জন্যে। সেখানেই দেখা হত। সে বাড়িতে দেখা হত, যখন শিলি যেত তামাহাটে। আবার সাইকেল নিয়ে সেও এই কুমারগঞ্জে চলে আসত, তামাহাট থেকে। শিলি ভেবেই আনন্দ পেত যে, সে আসত, হয়তো শিলিকে শুধু একবার দেখতেই। হয়তো সত্যিই তাই আসত। কলকাতার কোনো ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়ত সে। কলেজের নামটা ভুলে গেছে শিলি।
ছেলেটির গায়ের রং ছিল মাজা। কিন্তু খুব লম্বা। মাথা-ভরতি চুল, সুন্দর, শক্ত চেহারা। ধবধবে সাদা ধুতি-পাঞ্জাবি পরত, নয়তো হাওয়াই শার্ট আর প্যান্ট। তাও সাদা। ছেলেটির মধ্যে শুধু শিক্ষাই ছিল না, সহবত সম্ভ্রান্ততা সব-ই ছিল। বড়োঘরের ছেলে বলতে শিলির মা চিরদিন যা বোঝাতেন, তার সবই ছিল সেই হিতেন বোস-এর মধ্যে। শিলির জ্ঞাতি সম্পর্কে কাকা হত তাই হিতুকাকু বলে সম্বোধন করত শিলি তাকে। একটা পুরো মাস, বর্ষায় চ্যাগারের পাশের গাছের গন্ধরাজ ফুলের গন্ধর-ই মতো তাকে আমোদিত, আনন্দিত, শিহরিত করে রেখে, হিতেন ফিরে গেছিল কলকাতায়।
যখন ছিল এখানে, তখন আলোকঝারি পাহাড়ে শিলি তার সঙ্গে সাতবোশেখির মেলায় গেছিল। শিকারের শখও ছিল ছেলেটির। ধুবড়ির পূর্ণবাবুর দোনলা বন্দুক চেয়ে নিয়ে এসেছিল সে। শিলির মারকুইট্টা কাকার সঙ্গে, পর্বতজুয়ারে চিতাবাঘ আর শুয়োরের খোঁজে যেত হিতেন। ওসব একদিনও পায়নি। ফিরে আসত প্রায়-ই সোনালি বনমোরগ সাইকেলে বেঁধে। অবশ্য লালচে কুটরা হরিণ মেরেছিল একদিন। কাকা আর হিতুকাকু দু-জনে মিলে কষ্টে-সৃষ্টে টুঙ বাগানের মধ্যে দিয়ে বয়ে এনেছিল কুটরা হরিণটাকে।
রক্তারক্তি, মারামারি শিলি যে, পছন্দ করে না, একথা বলার পরদিন থেকেই হিতুকাকু বলেছিল, যে-ক-দিন এখানে আছি শিলি, আর কিছুই শিকার করব না; হিংস্র কিছু ছাড়া।
হিংস্র কিছু মানে? কী কী?
–বাঘ, ভাল্লুক, চিতাবাঘ, বিষাক্ত সাপ, আর এই ধরো তোমার মতন সুন্দরী মিষ্টি-হাসির কোনো মেয়ে!
-আহা!
বলেছিল, শিলি।
লজ্জাতে শিলির গাল লাল হয়ে গেছিল।
তারপরে হিতুকাকু চলে গেলে, দেওয়ালের আয়নার সামনে দাঁড়িয়েছিল শিলি এসে। পড়ন্ত বেলায় নরম কমলা রোদ, কালোজাম গাছের পাতার ঝালরের ফাঁক-ফোঁকর দিয়ে এসে পড়েছিল। ঘরময়। শিলির চুলে, মুখে। কমলার সঙ্গে বেগুনি আভা মিশে গেছিল যেন সেই আলোয়।
কালোজামের পাতারাও কি বেগুনি হয়? আলোমাখা কালোজামের পাতাদের দিকে চেয়ে ভেবেছিল ও।
কী বা আছে তার? ভেবেছিল, শিলি। জোড়া ভুরু, কুচকুচে কালো রং। নাকটি অবশ্য বেশ টিকালো, চোখ দুটি বড়ো বড়ো বড়ো বড়ো চোখের পাতা আর পল্লব। দাঁতগুলোও খুব
একটা খারাপ নয়। মন্দ কী?
নিজেকেই নিজে বলেছিল শিলি। শিলির মা বলতেন, মেয়েদের সবচেয়ে বড়ো প্রসাধন হচ্ছে দুটি। একটা হল যৌবন। অন্যটি বুদ্ধি। যৌবন চলে গেলে, যতই সাজো লাভ নেই। যৌবনের দীপ্তিটাই আলাদা। আর বুদ্ধি না থাকলে, গায়ের ধবধবে রং, স্নো, পাউডার, রুজ কিছুতেই তার অভাব ঢাকা পড়ে না। প্রত্যেক মেয়েকেই যৌবন এক আলাদা শ্ৰী দেয়, দীপ্তি দেয়। যৌবনে কুকুরিকেও সুন্দরী দেখায়।
কে জানে! হিতুকাকু কী দেখেছিল তার মধ্যে।
অদ্ভুত দৃষ্টিতে এই গেঁয়ো শিলির দু-চোখে তাকিয়ে থাকত। অসভ্যর মতন নয়। দারুণ এক দৃষ্টিতে, বোধ হয় কবি-টবিরা এমন চোখে তাকান, যাঁদের নিয়ে তাঁরা কবিতা লেখেন, তাঁদের দিকে। গা শিরশির করে উঠত শিলির। হিতুকাকুর সেই চাউনি যেন, তার আপাদমস্তক লেহন করত কিন্তু তাতে কোনো অশালীনতা ছিল না, নোংরামি ছিল না। হিতুকাকু মানুষটার মধ্যে কোনোরকম নোংরামিই দেখেনি শিলি। এমন পুরুষ জীবনে কম-ই দেখেছে।
চলে যাওয়ার সময় শিলির একটা ফোটো চেয়েছিল হিতুকাকু। সম্প্রতি তোলা ফোটো নেই শুনে, তামাহাটের পিন্টুদাদের বাড়ি থেকে ক্যামেরা ধার করে এনে, আদর করে শিলির ফোটো তুলেছিল। কলকাতায় ফিরে গিয়ে তাকে সেই ফোটো আর একটি সুন্দর চিঠি পাঠিয়েছিল হিতুকাকু। এমন সুন্দর কাগজে, এমন সুন্দর ভাষায়, অমন নরম, ভদ্র ভালোবাসার চিঠি যে, কেউ লিখতে পারে তা ওই চিঠি না পেলে জানতেও পেত না। একটি চিঠি যে, রুখু মনের মধ্যেও সব ফুলগুলি কীভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারে, তা হিতুকাকুর চিঠি না পেলে সত্যিই জানত না কখনো শিলি।
একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল শিলি, ঘাড়ে আর পিঠে সাবান মাখতে মাখতে, স্নান করতে করতে।
মা চলে যাওয়ার পর, এ বাড়িতে দ্বিতীয় কোনো মেয়ে নেই বলে, কতদিন যে, পিঠে ভালো করে সাবান দিতে পারে না। একদিন ও-বাড়িতে গিয়ে হোন্দলের মাকে দিয়ে পিঠ ঘষাবে ঠিক করল।
হিতুকাকু এখন বম্বেতে বড়ো চাকরি করে নাকি। বিয়েও করেছে গতবছর। ছেলে-মেয়ে নাকি হয়নি এখনও। হিতুকাকুর বউ-এর ছবি দেখতে খুব ইচ্ছে করে, শিলির। সে কি শিলির চেয়েও সুন্দরী? শুনেছে, খুব-ই সুন্দরী। শহরের সুন্দরী। বি. এ. পাশ। মোটরগাড়ি দিয়েছে নাকি মেয়ের বাবা হিতুকাকুকে, বিয়েতে। ছেলেগুলো বড়ো বোকা হয়। শিলিরও দেওয়ার অনেক কিছুই ছিল। বিয়ে করলে, তবেই না জানতে পেত হিতুকাকু। সেই শহুরে মেয়ে কি, তার মতো খেজুরে গুড়ের পায়েস রাঁধতে পারে? নতুন চালের পাগল-করা গন্ধের ফেনাভাত? বড়ো বড়ো কইমাছের হর-গৌরী? একপাশে–মিষ্টি, একপাশেঝাল? হিতুকাকুর বউ, বড়ো চিতল মাছের তেলঅলা পেটি কি রান্না করতে পারে শিলির মতো? কাঁচালঙ্কা, কালোজিরে ধনেপাতা দিয়ে? চিতলের মুইঠ্যা? মাঝারি শিঙি মাছ দিয়ে কালোজিরে-কাঁচালঙ্কা-বেগুন আর পেঁয়াজ দিয়ে গা-মাখা চচ্চড়ি? ঝাল-ঝাল, ঝাঁঝ-ঝাঁঝ? গঙ্গাধর নদী ডুব-সাঁতারে এপার-ওপার করতে পারে কি? সেই বড়লোকের মেয়ে? গাছ কোমর করে শাড়ি পরে, সিঁদুরে-আমের গাছের মগডালে চড়ে আম পেড়ে খাওয়াতে পারে হিতুকাকুকে? চটের ওপর রঙিন মিষ্টি-মিষ্টি গন্ধর নতুন পাট দিয়ে লিখতে পারে কি God is good অথবা Do not forget me? সে কি বিশ্বাস করে মনে-প্রাণে যে, সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে? শিলিরও দেওয়ার অনেক কিছুই ছিল। সব দানের কথা আলোচনা করা যায় না। কিন্তু ছিল যে, তা শিলিই জানে। অনেক এবং অনেকরকম দান।
গা-মাথা মুছে ফেলল শিলি। বাবার বার্লিটা জ্বাল দিতে হবে। পিউরিটি বার্লি ছাড়া অন্য বার্লি আবার বাবার মুখে রোচে না। মা খেতে ভালোবাসতেন হান্টলি-পামারের বিস্কুট। দু একবার-ই খেয়েছিলেন অবশ্য। বাবা কাকে দিয়ে যেন আনিয়েছিলেন, কলকাতা থেকে।
এসব ভেবে আর কী হবে? চলে-যাওয়া দিনের কথা। দূরে-থাকা আদর্শ পুরষের কথা ভেবে?
তবু, ভাবনা তো শুধু মানুষের-ই বিশেষ গুণ। ভগবানের বিশেষ দান। ভাবতে, সব জীব ই তো আর পারে না।
.
ম্যানেজারবাবুর বাংলোর বারান্দার সাদা রং-করা বেতের চেয়ারে বসে, কাঁচের টেবিলের ওপরে রাখা, সুন্দর দেখতে, বম্বের পেডার পটারির টি-পট থেকে ঢেলে চা দিচ্ছিল পুতনকে, ম্যানেজারবাবুর মেয়ে রুচি।
দার্জিলিং-এর লরেটো কলেজে পড়ে সে। কথায় কথায় কাঁধ-ঝাঁকিয়ে, ববকাট চুল উড়িয়ে, ইংরিজি বলে।
ঘোর লেগে যায় পুতনের। এ এক নতুন জগৎ!
উলটো দিকের চেয়ারে পুতন এবং রুচির কলকাতা থেকে আসা কাজিন, রাজেন বসে আছে।
কুমারগঞ্জ গ্রামের অতিসাধারণ অবস্থার ছেলে পুতন প্রথম প্রথম এমন পরিবেশে কুঁকড়েই থাকত। কী করবে, কী বলবে, বুঝে উঠতে পারত না। তার বাঙালত্ব নিয়ে বাগানের অনেকে তো বটেই এবং খাস কলকাতার ঘটি মানুষ ম্যানেজারবাবুও বেশ একটা ঠাট্টা-তামাশাও করতেন।
বাগানের মালিক এখন আর বাঙালি নেই। মাত্র তিনমাস আগে এক মারোয়াড়িকে দিয়েছেন আগের মালিক। সেই মারোয়াড়ি ব্যবসায়ীর ব্যাবসাও কলকাতাতেই। আগের মালিক কলকাতার বাঙালি ছিলেন বলেই কুলি-কামিনরা ছাড়া কলকাতার লোক-ই বেশি, এই বাগানে।
প্রথম প্রথম গেলুম, খেলুম, নুন, নঙ্কা, নুচি, নেবু এইসব শুনে ভিরমি খেত পুতন। কিন্তু বেশিদিন পতিত থাকার চরিত্র নিয়ে পুতন জন্মায়নি। কিছু মানুষ, পাটিগণিতের বইয়ের তৈলাক্ত বাঁশে-চড়া বাঁদরের মতো প্রচন্ড অধ্যবসায় নিয়েই জন্মায়। পুতন, সেই উচ্চাকাঙ্ক্ষীদের শ্রেণিতে পড়ে। যেহেতু ম্যানেজার এবং বাগানের অধিকাংশ অফিসার কলকাতার লোক, পুতন অচিরে শুধু তার বাঙালত্বই যে, বিসর্জন দিয়েছে তাই-ই নয়, তাদের সঙ্গে সমানে করলুম খেলুম, মলুম, শুলুমও করে যাচ্ছে। শেয়াল যেমন হালুম হুলুম ডাক ছাড়তে পেরে কখনো-সখনো শ্লাঘা বোধ করে যে, সে বাঘ হয়েছে; পুতনও তেমন খেলুম, শুলুম, নুন, নঙ্কা, নুচি-বলে বলে তার অকারণের হীনম্মন্যতাকে গলা টিপে মেরে ফেলে, খাস কলকাতার লোক হয়েছে ভাবতে লাগল।
এদিকে খাস কলকাতার লোকেরাও যে, আজকাল হুম হুম ছেড়ে, খেয়েছিলাম-এ ফিরে আসছেন গেসলুম ছেড়ে গেছিলাম-এ সেটা নকল করার মতো বিদ্যেবুদ্ধি পুতনের ছিল না। অনুকরণের বিদ্যে অনেক সহজ, ওরিজিনালিটির শিক্ষা তা নয়। প্রোটোটাইপ সহজে হওয়া যায়, ওরিজিনাল ওরিজিনাল হতে পারেন। তাকে নিয়ে খাস কলকাতার লোক এবং খাস পূর্ববাংলার মানুষেরা সকলেই যে, একইসঙ্গে সমানে হাসাহাসি করে, সে-কথা বোঝার মতন বুদ্ধি পুতনের ছিল না। বুদ্ধি পুতনের কোনোদিন-ই বিশেষ ছিল না। অধিকাংশ মানুষ দুর্বুদ্ধি আর সুবুদ্ধির মধ্যে যে-তফাত আছে, তা কোনোদিনও নিজেরা পুরোপুরি বোঝে না। তাদের জাগতিক উন্নতির জন্যে, যেকোনো ফলপ্রসূ বুদ্ধিকেই তারা সুবুদ্ধি বলে মনে করে। উচ্চাকাঙ্ক্ষী পুতন সেই, গরিষ্ঠদের জনগণের দলে।
রুচির পোশাকআশাক, জামাকাপড়, হাসি, সব-ই ঘোর লাগায় পুতনের মনে। তবে ও বোঝে যে, রুচির দিকে হাত বাড়ালে তার হাতটাই যাবে কাটা। তা ছাড়া মালিকানা বদলের পর ম্যানেজারবাবুর মাথাটাও যে ধড়ের ওপরে বেশিদিন হয়তো নাও থাকতে পারে, এ জ্ঞানটাও পুতনের ছিল না। এই সময়ই কলেজের ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিয়ে রুচির এক মামাতো বোনও এসেছে এখানে বেড়াতে। ওদের বাড়ি বর্ধমানের কোনো গ্রামে। মেয়েটির মাজা রং, গালে একটি কাটা দাগ। গ্রামের মেয়ে হলেও বুদ্ধি যে, সে রাখে তীক্ষ্ণ, তা দেখলেই বোঝা যায়। কিন্তু তার পোশাক-আশাক এবং আড়ষ্টতা দেখে মনে হয় যে, তাদের অবস্থা বিশেষ ভালো নয়, এবং রুচিদের কৃপাপ্রার্থী তারা। সবসময়েই সে, এই পরিবারের মন জুগিয়ে চলে। নানা ব্যাপারেই পুতন, রুচির সঙ্গে সেই মেয়েটির এই তারতম্য লক্ষ করে। খাওয়ার সময়ে খাওয়ার টেবিলে বসে ম্যানেজারবাবু এবং রুচি এবং রুচির ছোটোমামা রাজেন এমনকী রুচির মা এবং ছোটোভাইও একইসঙ্গে খেতেন। তাঁদের খাওয়া-দাওয়া দেখাশোনা করত, সেই মেয়েটিই। অলকা তার নাম।
রুচির মা একদিন বলেছিলেন, অলকাকেই; অলি আমাদের খুব-ই কাজের মেয়ে। এই ক-দিন একটু যত্ন-আত্তি করত মা আমাদের।
অলি খেতে বসত, বাড়িসুদ্ধ সকলের খাওয়ার পর বাবুর্চিখানার মেঝেতে। কোনোদিন বা একটা টুলের ওপর বসে, কোলের ওপরে অ্যালুমিনিয়ামের থালা নিয়ে সে খেত। প্রায় বাবুর্চি-বেয়ারাদের মতো। লক্ষ করেছিল পুতন। অন্যরা খাওয়া-দাওয়ার পর খাটে শুয়ে বা চওড়া বারান্দায় বসে যখন নভেল পড়তেন বা ম্যাগাজিনের পাতা ওলটাতেন অথবা ছায়াচ্ছন্ন পাখিডাকা বাগানে দোলনা চড়তেন, তখন অলি আচার আর পাঁপড় বানিয়ে উবু হয়ে বসে, ঘুরে ঘুরে শুকোতে দিত বাগানের-ই এককোনায়।
অলিকে দেখে পুতনের দুটো জিনিস মনে হত। প্রথমত, অনেক-ই দিক দিয়ে অলকা পুতনের শ্রেণির। যদিও অমিলও ছিল অনেক। তাকে বিয়ে করতে যদি পারে পুতন, তাহলে পুতন এক নতুন জাতে উঠবে। এই চা-বাগানে বাঙাল বলে তার যে-হেনস্থা, তা ঘুচবে।
দ্বিতীয়ত, ম্যানেজারবাবুর আত্মীয়াকে বিয়ে করায় তার উন্নতি অনিবার্য। গরিব আত্মীয়দের সচরাচর বড়োলোকেরা এড়িয়েই চলেন। কিন্তু যে-আত্মীয় চোখের সামনে জলজ্যান্ত থাকে তাকে একটু মর্যাদা নিজেদের খাতিরেই দিতে হয়। অন্যকিছু না হলেও, লোকভয়ের-ই কারণে। তা ছাড়া, প্রায় মরে-যাওয়া বিবেকও হঠাৎ হঠাৎ জেগে উঠে মৃগী রোগীর মতো খিচুনি দিয়ে হাত-পা ছুঁড়তে থাকে বলেও।
শিলির কথাও মনে যে, পড়ে না পুতনের তা নয়। কিন্তু তাকে সে বিয়ে আদৌ করবে না। করা সম্ভব নয়। বিয়ের সঙ্গে প্রত্যেক বুদ্ধিমান, প্র্যাকটিক্যাল পুরুষ ও নারীর সমস্তটুকু ভবিষ্যৎ জড়িত। যে-মূর্খরা একথা না বোঝে তাদের কপালে দুঃখ অবধারিত। এবং তা খন্ডাতে পারে, এমন কেউই নেই। স্বয়ং ভগবানও না।
অনেক-ই ভেবে দেখেছে পুতন। শিলিকে বিয়ে করলে, শিলির বাবার দায়িত্বও পুতনকে নিতে হবে। তার নিজের মায়ের দায়িত্ব তো আছেই তার ওপরে।
রুচির ছোটোমামা রাজেন ছেলেটা যদিও তার সমবয়সি, কিন্তু একটু অদ্ভুত ধরনের। পুতনের সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠ হতেই এবং ওকে একা পেতেই বার বার বলেছে, কী গুরু! চা বাগানে এলুম, দু-টি পাতা একটি কুঁড়ির জায়গাতে, দু-একটি কুঁড়ি-ফুড়ি একটু দেখাও। কুঁড়ি ফুটিয়ে ফুল করি। যেমন শুকনো পাতা ফুটিয়ে চা করি। নানারকম আদিবাসী কামিন-টামিন…
প্রথম প্রথম বুঝতে পারেনি গাঁয়ের সরল ছেলে পুতন, কথাটা। কারণ পুতনের ওসব দিকে কোনো উৎসাহ-ই ছিল না। কুলি-লাইনের কোন কোন ঘরে, কেমন মেয়ে আছে এবং কোন কোন কামিনেরা পয়সার বিনিময়ে দেহ দেয়, তা সে জানত না। জানার কোনো ঔৎসুক্যও ছিল না। তবে, কেউ কেউ যে দেয়, তা সে অফিসের বাবুদের কানাঘুসোয় শুনতে পেত।
ম্যানেজারবাবুর বাড়িতেই একটি মেয়ে কাজ করে। সে মেয়েটি নাকি ম্যানেজারবাবুর-ই রক্ষিতা। দারুণ দেখতে কিন্তু মেয়েটি। বছর কুড়ি বয়স হবে। কাটা-কাটা চোখ-মুখ, তেমন-ই শরীর, বেশ লম্বা, কোমর অবধি চুল।
ম্যানেজার সাহেবের বউ, বর্ষার সময় যখন কলকাতায় যান বাপের বাড়ি, একেবারে পুজো কাটিয়ে আসবেন বলে, তখন সেই মেয়েটিই নাকি ম্যানেজারবাবুর স্ত্রী হয় রাতে।
পুতন অবশ্য সহজেই বাগানের অন্য কারও সাহায্যে কলকাতার রাজেনবাবুর জন্যে বন্দোবস্ত করতে পারত। কিন্তু তাহলে রাজেন যে, তার হাত ছেড়ে দিয়ে অন্যের খপ্পরে গিয়ে পড়ত। রাজেনকে হাতছাড়া করে এমন বোকা পুতন নয়। রাজেন-ই এখন ম্যানেজারবাবুর বাড়ির সঙ্গে পুতনের একমাত্র সেতু। সেতু ভেঙে যাক, তা সে চায় না।
কী ভেবে, পুতন হঠাৎ একদিন রাজেনকে আশ্বস্ত করে বলেই ফেলল যে, আজকাল নানারকম প্রবলেম বাগানে। পলিটিক্যাল পার্টি-ফার্টি আছে। তিলকে তাল করে এরা। কামিনদের মধ্যেও শিক্ষার প্রসার হয়েছে। আগেকার দিনের মতন কোনো শালার জোতদারি নয় তারা। তা ছাড়া, কোনোরকমে জানাজানি হলে ম্যানেজারবাবু পর্যন্ত বিপদে পড়বেন। সবচেয়ে আগে চাকরিটা যাবে তাঁর-ই। এখানে কিছু হবে না। তার চেয়ে চলো আমার সঙ্গে, আমাদের দেশের বাড়িতেই বরং। আমার হাতেই আছে একটি। আমি যা বলব, তাই-ই সে করবে। আ বার্ড ইন হ্যাঁণ্ড ইজ ইকুইভ্যালেন্ট টু টু, ইন দ্যা বুশ।
–জিনিস কেমন?
রাজেন ভুরু তুলে, সিগারেটে টান দিয়ে, লাল-লাল চোখ নাচিয়ে বলেছিল।
–কেমন আর! গেঁয়ো জিনিস যেমন হয়। তেমন আর কী। তবে…ভালো।
–আনটাচড তো?
–এক্কেবারে। সেটুকু বলতে পারি। গ্যারান্টি।
–গুরু, তুমি নিজে? নিজেও কি দু-একটি পাঁপড়ি ছেঁড়োনি?
–ছিঃ?
বলেছিল, পুতন। হঠাৎ-বিবেকের কামড় খেয়ে। বিবেক হচ্ছে, বিছের মতন জিনিস। কোথায় যে, কোন চিপুতে লুকিয়ে থাকে, আর কখন যে, হঠাৎ বেরিয়ে পড়ে কামড় দেয় মানুষকে, তা যারা বিবেক অথবা বিছে এ দুয়ের একটিকেও জানে; তারাই জানে!
পুতনের দু-কান গরম, লাল হয়ে ঝাঁ ঝাঁ করছিল।
একথা ঠিক যে, পুতন ছেলেটার স্বচ্ছল জীবনের প্রতি বড়োলোভ। শিশুকাল থেকে। অর্থাভাবের জন্য বহুরকম কষ্ট ও অসম্মানকে সে জেনেছিল। তবু এখনও তেমন অন্যায় কিছু করেনি, সেই লোভের বশবর্তী হয়ে। খারাপ হয়নি এখনও। জানে না, কোনোদিনও খারাপ হবে কি না। তবে খারাপ হতেও যে, ভালো হওয়ার চেয়ে কম কষ্ট হয় না; এই খারাপ কথাটা রাজেনকে বলে ফেলেই ও বুঝতে পারল। বুঝল পুতন, বি-কম-এ ফাস্ট ক্লাস পাওয়াটা যেমন কষ্টের, শিলিকে তার নিজের উন্নতির জন্যে রাজেনের ভোগে লাগতে দেওয়াও তার চেয়েও অনেক-ই বেশি কষ্টের। এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকাটাই বড়োেকষ্টের। যে, যেমন করেই বাঁচুক-না-কেন।
পুতনের ছি : শুনেই, খুব জোরে হেসে উঠেছিল রাজেন।
তারপর ডান হাতের তিন আঙুল দিয়ে ওর থুতনি নেড়ে দিয়ে বলেছিল মা-ন-তু।
–আমি ওসব লাইনেই নেই।
পুতন বলেছিল। রেগে।
আবারও বলেছিল, রাজেন।
-মা-ন-তু!
বলে, আবারও পুতনের থুতনি নেড়ে দিয়েছিল জোরে। বলেছিল, নেকুপুষুমুনু আমার।
পুতন মোটেই দুশ্চরিত্র নয়। কখনোই কোনো মেয়ের সঙ্গে ও কিছুমাত্রই করেনি। গতবার যখন দেশে গেছিল, তখন এক দুপুরবেলায় শিলিকে আমবাগানের ছায়ায় একটা চুমু খেয়েছিল শুধু। তাও, জোর করে, ওকে গাছে চেপে ধরে। উ-উ-উ-উমম করে আপত্তি জানিয়েছিল শিলি। কিন্তু পুতন বুঝেছিল যে, ভালো লেগেছিল শিলির। কোনো মেয়েকে আদর করতে গায়ের জোরের চেয়ে ভালোবাসাই যে, অনেক বেশি লাগে, তা সেই দুপুরেই প্রথম জেনেছিল ও। উত্তেজনা, পুতনেরও কম হয়নি। সমস্ত শরীরে কত যে, নাম-না-জানা অনুভূতি আকুলি-বিকুলি করে উঠেছিল ঝড়ের দোলালাগা ফুলের-ই মতন, তা কী বলবে। নারীশরীরের ওই অদেখা-অজানা-অসীম রহস্যের আভাস পেয়েই উত্তেজনায় কেঁপেছিল। ভেবেছিল, একটি চুমুতেই যদি এত উত্তেজনা, তবে আরও বেশিকিছু হলে হয়তো উত্তেজনাতে মরেই যাবে। ভালোলাগাটা এতই বেশিভালো যে, খারাপ লেগেছিল ওর। ভেবেছিল পুতন, সমস্ত ভালো জিনিস-ই, অথবা নেশার জিনিস-ই, প্রথম প্রথম বোধ হয় খারাপ লাগে। মদের-ই মতো।
চাকরিতে উন্নতি করতে হলে, একটু মদ-টদও নাকি খেতেই হয়। ম্যানেজারবাবু নিজেই বলেছিলেন একদিন।
বাগানের মালিক যদিও মারোয়াড়ি, তাঁর শখের অভাব নেই। সবরকম সাহেবিয়ানাতেই তিনি পোক্ত হয়ে উঠেছেন। ইংরিজি উচ্চারণটা যদিও পুতনের চেয়েও খারাপ। তাতে কী এসে যায়? মালিকেরা খোদার সৃষ্ট অন্য গ্রহের জীব। তাঁদের কোনো গুনাহ নেই। তাঁরা যাই করুন-না-কেন, বেহেস্ত-এর দরজা তাঁদের জন্যে সবসময়ই খোলা। মালিকের কাজ করতে হল, উন্নতি করতে হলে, মালিকের গু-কেও সুগন্ধি বলতে হয়।
লোকে বলে, ম্যানেজারবাবুর সঙ্গে মালিকের বন্দোবস্ত আছে। ম্যানেজারবাবুর বাংলোর ওই মেয়েটিকে ডিরেক্টরস বাংলোতে ডিউটিতে যেতে হয়, মালিক এলেই।
ব্যবসাদার মাড়োয়ারিরা শুধু কাজ আর টাকা-পাগলা বলেই জানত এতদিন পুতন। এমন গুণী মাড়োয়ারির কথা, সে আগে শোনেনি। আজকাল নাকি গুণীদের সংখ্যা বেড়েই যাচ্ছে, বিশেষ করে কমবয়েসিদের মধ্যে। একথাও শুনতে পায় অনেকেরই কাছে।
পুতন ঠিক করেছে শিলিকে ও তুলে দেবে রাজেনের-ই হাতে। একদিনের জন্যে বই তো নয়, তুলে দেবে হুলোবেড়ালের মতন কলকাতার রাজেনের মুখে; অনভিজ্ঞ, বিন্দুমাত্র সন্দেহহীন শিলিকে, কালো, নরম কবুতরীর মতো। কালো কবুতরীরও ভেতরের দিকে তো সাদা পালক থাকেই। নরম, মসৃণ সেইসব পালক রাজেন ছিন্নভিন্ন করবে, একথা কল্পনা করেই পুতনের মনেই একধরনের তীব্র বিকৃত আনন্দ হচ্ছিল।
শিলির বাবা নরেশবাবু যদি জানতে পারেন? জানলেও কী? কিন্তু পরেশকাকু? সে জানলে, কী করবে কিছুই ঠিক নেই। অ্যালফাম্যাক্স এল. জি. দিয়ে, ধুনে দেবে হয়তো পুতন আর রাজেনকে। নরেশকাকু করতে পারে না, এমন কাজ নেই। ভালো কাজ। আর সঙ্গে আবু ছাত্তার থাকলে তো কথাই নেই। সোনায় সোহাগা।
রাজেন অবশ্য পুতনকে বলেছে, চিন্তার কিছু নেই গুরু; পেট করে দেব না। অমন কাঁচামাল আমি নই। সোনাগাছির রেগুলার খদ্দের আমি। তাইতো মাঝে মাঝে তামাগাছি, রুপোগাছি, পেতলগাছি, দেখতে একটু ভালো লাগে। আমার সঙ্গে কনট্রাসেপটিভ থাকে সবসময়ই। ডাক্তারের ব্যাগে, যেমন রুগির জন্যে কোরামিন ইঞ্জেকশন থাকে। কখন কোথায় যে, দরকার হয়, কে বলতে পারে? বলো, গুরু? সবসময় প্রিপেয়ার্ড থাকতে হয়। যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখো তাই, পাইলেও পাইতে পারো অমূল্য রতন। কে বলেছিল জান কি?
কে?
–নাই বা জানলে।
–সীতার বাপের নাম জান কি?
পুতন চুপ করে থাকল। মানা করা সত্ত্বেও রাজেন কোয়ার্টারে বসে বেশি মাল খেয়ে ফেলেছে। ওটার নাম ভুটান অরেঞ্জ। ভুটানি হুইস্কি। এসব কি আলু-পোস্ত খাওয়া উত্তর কলকাতার শৌখিন লিভারে নেয়? ঠেলাটা বোঝো এবার। ভুটান-অরেঞ্জ এসেছে ফুন্টসোলিং থেকে।
পুতন ভাবে, এসব গর্ভ-টর্ভর ঝামেলা না হলেই হল। চুরিবিদ্যা বড়ো বিদ্যা, যদি না পড়ো ধরা। রাজেন তাকে একদিনে অনেক-ই শিখিয়েছে। রোজ সন্ধেবেলা মংলুকে দিয়ে দিশি মদ আনিয়ে খাচ্ছে পুনের কোয়ার্টারে বসে, দু-জনে।
আজকের ভুটান অরেঞ্জ-ই গোলটা বাধাল।
সিগারেটে বড়ো বড়ো টান দিতে দিতে রাজেন বলেছিল, ছাড়ো তো গুরু। ছাড়ো, ছাড়ো! আমার হাতে নতুন পাখি পড়লে এমন বুলি শেখাব না, যে, বাকিজীবন শুধু এছাদ-ওছাদ, ওডাল-সেডাল করে উড়ে বেড়াবে, খুঁটে খাবে। সে পাখি আর কোনো ছা-পোষা কেরানির ঘরে পোষ-ই মানবে না।
খারাপ যে লাগে, তাও নয়। যদিও এক নিষিদ্ধ, অনাঘ্রাত, অদেখা-অজানা জগৎ তার চোখের সামনে দিয়ে শীতের দুপুরের মন্থরগতি দাঁরাশ সাপের মতোই যেন ধীরে ধীরে চলে যায়, জলপাই গাছের ছায়ায় ছায়ায়।
পুতন, ম্যানেজারবাবুর বাংলো থেকে নিজের কোয়ার্টারের দিকে ফিরে যেতে যেতে ভাবছিল এতসব কথা। বাগানের চা-গাছে ছায়া-দেওয়া, বড়ো বড়ো রেইনট্টির মতন গাছগুলোর ছায়া নেমেছে, ঘন হয়ে। কী নাম গাছগুলোর? কে জানে! দূরে, তিস্তার ফিকে গেরুয়া চর দেখা যাচ্ছে। তার ওপাশে তরাই-এর জঙ্গলের রোমশ বাইসনদের প্রকান্ড এক দলের মতো হিমালয় পর্বতশ্রেণি কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে আদিগন্ত ছড়িয়ে আছে। বেলা পড়ে আসছে। পাখিরা ঘরে ফিরছে। দু-টি বড়ো ধনেশ হাওয়ায় ডানা-ভাসিয়ে দিয়ে সূর্যের দিকে চলেছে, নিষ্কম্প। গ্লাইডিং করে।
ভালো যেমন লাগে, আবার মনটা খারাপও যে, লাগে না, তাও নয়।
শিলি মেয়েটা পুতনকে সত্যিই ভালোবাসত। সবচেয়ে বড়োকথা, পুতনের মা কিরণশশী, শিলিকে খুবই ভালোবাসেন। মায়ের খুব-ই ইচ্ছে যে, সে বিয়ে করে শিলিকে।
কিন্তু মা কী জানেন? কী জানেন মা? কতটুকু জানেন এই পৃথিবীর? এই ব্যাবসার জগতের ক্রিয়াকান্ডর? উন্নতির সিঁড়ির কথা?
তা ছাড়া, মা আর কতদিন-ই বা বাঁচবেন? অলকাকে বিয়ে করলে ম্যানেজারবাবুর আত্মীয়া সে, তাকে নিয়ে গিয়ে কুমারগঞ্জ-এর ভাঙাবাড়িতে রাখা যে, আদৌ যায় না, একথা মাকে সহজেই বোঝানো যাবে। কানাঘুসো শুনছে এখানে যে, আরও একটি বাগান নাকি নিচ্ছেন ওদের মালিক, ভুটানের বর্ডারে। মালিকের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি মানে, তাদেরও সমৃদ্ধি। এসব কথা জেনে, মালিকের কুৎসিত, বদমাইশ-বদমাইশ মুখখানিকেও বড়ো সুন্দর, অপাপবিদ্ধ বলে মনে হয় তার দু-চোখে।
সংসারে টাকার মতো সুগন্ধি, এমন সুন্দর মুখোশ আর কিছুই নেই বোধ হয়।
নতুন বাগান নেওয়া হলে, পুতনকে নাকি সেই বাগানে প্রমোশন দিয়ে পাঠানো হবে। বেশি মাইনে, ভালো কোয়ার্টার, স্কুটার।
একটা জিনিস-ই শুধু খারাপ। বুনোহাতির বড়ো অত্যাচারের কথা শোনে ভুটানের কাছে। তা, পয়সা রোজগার করতে হলে, মালিকের লাথির মতো হাতির লাথিও খেতে হবে বই কী। শিলিকেও তুলে দিতে হবে রাজেনের হাতে। বেড়ালকে কবুতর সাপ্লাই করতে হবে। পয়সা রোজগার আর অর্ডার-সাপ্লাই ব্যাপারগুলো একেবারেই জড়িয়ে-মড়িয়ে গেছে। পুতনের নিজের চরিত্রটা অবশ্য ফাস্ট-ক্লাস। অকলঙ্ক সে। থাকবেও তা।
পুতন বোঝে যে, সে বদলে গেছে। প্রতিদিন বদলে যাচ্ছে। গ্রাম থেকে কাশফুলের গন্ধে নাক আর ঘুঘুর ডাকে কান ভরে নিয়ে যে-সরল, অল্পে-সন্তুষ্ট, সৎ, গ্রাম্য ছেলেটি একদিন কলকাতা গেছিল, সে আর বেঁচে নেই। সে অনেকদিন আগেই মরে গেছে।
যে-ছেলেটি একদিন এই চা-বাগানে এসেছিল, এম.কম পরীক্ষায় ফাস্ট-ক্লাস পেয়ে, ভবিষ্যৎ-এর অনেক সোজা-সরল সুখের স্বপ্ন বুকে করে, সেও বদলে গেছে অনেক-ই।
পুতন এতদিনে বুঝেছে যে, দু-রকমভাবে বেঁচে থাকা যায় জীবনে। এক, ম্যাদামারা, ল্যাজে-গোবরে; থিতু হয়ে বাঁচা। অন্য; উচ্চাশা, চাহিদা এবং নিত্যনতুন প্রাপ্তি নিয়ে দৌড়োতে দৌড়োতে ক্রমাগত নিজেকে বদলাতে বদলাতে বাঁচা। ও ম্যাদামারা জীবন চায় না। যেহেতু চায় না, তাই স্বাভাবিক কারণে প্রত্যেকদিন-ই সেই পুরোনো পুতনের মনের চেহারাটা একটু একটু করে বদলে যাচ্ছে—
বুঝতে পারে ও।
বাগানের কাজে একবার শিলিগুড়ি যেতে হয়েছিল ছুটি থেকে ফিরেই। নর্থবেঙ্গল ট্র্যাক্টর অ্যাণ্ড ফার্ম মেশিনারি থেকে তারা এবং আশপাশের অনেক বাগানেই ম্যাসি-ফার্গুসন ট্র্যাক্টর কিনেছিল। ট্র্যাক্টর রিপেয়ার করার জন্যে শিলিগুড়ি থেকে মিস্ত্রি আনতে পাঠিয়ে ছিলেন ম্যানেজারবাবু।
ট্র্যাক্টর কোম্পানি এবং নর্থবেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানির মালিকের সঙ্গে সেভক রোডের কনস্ট্রাকশন নিয়ে ব্যস্ত থাকায় সকালে দেখাই হল না। ওঁদের হিলকার্ট রোডের দোকান থেকে পুতনকে ওঁদের মোটাসোটা কর্মচারী রতনবাবু বললেন যে, বিকেলে আসতে। সেই নেপালি ভদ্রলোকও ছিলেন না। থাপা, না কী যেন নাম।
জিপের ড্রাইভার ঘুঘা বলল, চলেন যাই পুতনবাবু, ধুলাবাড়ি থিক্যা ঘুইরা আসি। ট্র্যাক্টর এখানেই আনন লাগব, যদি তাগো মেকানিক শ্যাষপর্যন্ত যাইতে না-ই পারে।
-ধুলাবাড়ি? সেখানে কী?
অবাক হয়ে বলেছিল, পুতন।
-আরে! ধুলাবাড়ির নাম শোনেন নাই? আপনারে নিয়া হত্যই চলে না। ন্যাপালের বর্ডার। পৃথিবীর সব জিনিস পাইবেন সেইখানে। একবার দেইখ্যা আইলে এক্কেরে চক্ষু সার্থক। লাইফ কারে কয়, চলেন, দেখাইমুনানে আপনারে।
ধুলাবাড়িতে যেতে হয় নকশালবাড়ির ওপর দিয়ে।
দারুণ অ্যান্টি-ক্লাইম্যাক্স।
এক জায়গার নামের সঙ্গে কিছু আদর্শবাদী বিপ্লবীর নাম জ্বলজ্বল করে, আর অন্য জায়গায়, চোরাচালানের মোচ্ছব। প্রয়োজনীয় এবং একেবারেই অপ্রয়োজনীয় সব বিলাসের ই মোচ্ছব সেখানে।
তবে, গিয়ে চক্ষু সার্থক হয়েছিল ঠিকই। কিন্তু তারসঙ্গে প্রচন্ড এক জ্বালা অনুভব করেছিল চোখে, গলায়, শরীরের সর্বত্র। টাগরা শুকিয়ে উঠেছিল। এত্ত জিনিস? একজন মানুষের সুখী হয়ে বাঁচতে এত্ত লাগে? এত জামা, গেঞ্জি, ট্রানজিস্টার হেয়ার-ড্রায়ার; রেকর্ড প্লেয়ার, টি.ভি. ছোটো-বড়ো, সাদা-কালো, রঙিন; বাজনা, ক্যালকুলেটর, কার্পেট-ক্লিনার, পারফিউম, নানা দেশের নানারকম কায়দার দাড়ি-কামানোর সরঞ্জাম।
শালার দাড়িকামানোরও যে, এত কায়দা ছিল তা ভাবনারও বাইরে ছিল।
মেয়েদের বডিস। প্যান্টি না কী বলে, কতরকম সাইজের।
কত-রঙা বোতলে বিলাইতি মদ। টাইপ-রাইটার। মায় কম্পিউটার পর্যন্ত।
জীবনে একজন মানুষের বেঁচে থাকতে হলে যে, এত জিনিসের প্রয়োজন হয় বা আদৌ হতে পারে, সেকথা কি হালার পুতন সরকার বাপের জন্মে কোনোদিনও ভাইব্যাছিল? এমন কইরা বাঁচনের নাম-ই বোধ হয় বাঁইচ্যা থাকা। এইসব দ্যাখনের পর সকাল-বিকাল দুগা ডাইল-ভাইত খাইয়া লুঙ্গি পইরা চৌকির উপর পাটি-বিছাইয়া শুইয়া থাইক্যা আর শিলির মতো একডা মাইয়ারে বউ কইরা আদর-টাদর, হুম-হাম দু-চারখানা চুমু-চামা খাইয়া খাওয়াইয়া, ছাওয়াল-পাওয়াল লইয়া ল্যাজেগোবরে বাঁইচ্যা থাকনের কথা আর ভাবন-ই যায় না। পিসারে পিসা! এ কী বাঁচনের আয়োজন কও তো দেহি। দুস শালা।
ড্রাইভার ঘুঘা আর পুতনকে দোকানি চা খাওয়াল।
সার-সার দোকান ধুলাবাড়িতে। সব-ই মাড়োয়ারিদের।
বাঙালি রিফিউজি মাইয়াগুলান, নানা বয়সি, খাড়াইয়া আছে। ওরাই নাকি জঙ্গলের মধ্য দিয়া নদী পারাইয়া স্মাগল-কইর্যা ন্যাপাল থিক্যা মাল লইয়া গিয়া শিলিগুড়িতে পৌঁছাইয়া দিয়া আসে। দামের উপর ক্যারিং চার্জ একটা লইয়া লয় দুকানিরা। মাইয়াগুলান নাকি রাতে রাতেই আসে। চেকপোস্টে ঘুসঘাস তো দ্যাওন-ই লাগে। আরও যে, কী কী দ্যাওন লাগে, তা জানে কেডায়? সব হালার গরমেন্ট-ই সমান। জ্যোতিবাবুদের অনেক-ই আশা কইরা ভোট দিছিল এই মাইয়াগুলানও। তা হইলডা কী? যে তিমিরে, হেই তিমিরেই। বাঙালি বইল্যা যে-একটা জাত আছে, ছিল কখনো; তাই-ই কইলকাতা বা শিলিগুড়ি দেইখ্যা বোঝনের উপায় পর্যন্ত নাই। ছ্যা:। বড় দুঃখে বুক ফাটে পুতনের। দুঃখ যখন হয়।
শোনলা কি তোমরা? পুতনেরও দুঃখ হয়।
মৃগেন কইতাছিল, আসানসোল, দুর্গাপুর, রানিগঞ্জেরও নাকি হেইরকম-ই হাল।
যাউকগা। পুতন তো আর ব্যাঙ্গলে স্যাটল করে নাই। বাঙালির প্রবলেম ব্যাঙ্গলের গভর্নমেন্টে বুঝুকানে। তারা তো এহনে আসামের মানুষ। যতদিন না খেদাইতাছে। বাঙালির না আছে জায়গা ব্যাঙ্গলে, না ব্যাঙ্গলের আউটসাইডে। পার্টিশন আর দিল্লির কর্তারা মিল্যা ব্যাঙ্গলিদের এক্কেরে মাইরা থুইছে না হালায়।
কী খিটক্যাল কী খিটক্যাল।
.
পুতন কী আর কিনবে?
একখানা চাইনিজ কলম, একবোতল রাশিয়ার সস্তা মদ। সাদা জলের মতো। তাই কিনল। এ হালায় আবার কী মদ কেডায় জানে? পেরছাপ না মদ, বোঝাই যায় না। আর একটা আমেরিকান লাল ব্যাঙ্গলনের গেঞ্জি, মাইনা পাছিল গতকাল। তার উপরে ঘুঘার কাছ থিক্যা ধারও নিল। হালার ধুলাবাড়িতে আইস্যা তো লাভের মধ্যে এই হইল। দুস শালা।
ঘুঘা জিপটা ইণ্ডিয়ার দিকে ঘুরিয়ে বলল, ক্যামন দ্যাখলেন, তাই কয়েন পুতনবাবু?
-কইস নারে। তুই আমার হকল হব্বোনাশ কইরা ফ্যালাইলি। আর ক্যা?
ঘুঘা, একটা বিলিতি সিগারেটে অমিতাভ বচ্চনের মতো দেশলাই ঠুকে বলল, ইটারেই লাইফ কয়। বোঝলেন, পুতনবাবু? লাইফ ইটারেই কয়। লাইফ ইনজয় করতে ব্যাশি কিছুর পেয়োজন নাই, বোঝলেন না, অনলি মানি। স-ই চাই। বাই হুক্কো অর বাই কুরোক্কো।
পুতন বুঝল যে, কথাটা বাই হুক আর বাই ক্রুক।
.
বাবার জ্বরটা দুপুরের দিকে কমেছে একটু।
তিনটে নাগাদ বাবা বললেন, পরেশ কি আইছে রে শিলি?
-না, এহনে কী? তার আইতে আইতে পরশু হইয়া যাইব গিয়া।
–পরশু! কইস কী তুই? গেছে কোনদিকে?
–কইয়া তো গেল, যমদুয়ার। সে কি ইখানে। হইব না পরশু?
শিলি বলল।
-যমদুয়ার?
হ।
নরেশবাবু কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন।
কাল রাতে গভীর জ্বরের মধ্যে একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছিলেন। তিনি যমের বাড়ি যাচ্ছেন। মস্ত একটা তোরণ। কোনো ফুল-টুল দিয়ে সাজানো নয়, রঙিন কাগজ বা কাপড়ের টুকরো দিয়ে সাজানোও হয়নি তা। জায়গাটাও ন্যাড়া শুনশান। একটা গাছ পর্যন্ত নেই। নদী নেই, ফুল নেই; শিশু নেই কোন, সেই দেশে। সেই মস্ত তোরণটা করা হয়েছে বাজে পোড়া একটা মস্ত শিমুলগাছ দিয়ে। সেই তোরণের কাছে কোনো পাহারাও নেই। ভেতরে একরকম ই দেখতে, এক-ই ডিজাইনের সার সার একতলা কালো-রঙা বাড়ি আছে। তাদের দরজা জানালা ছাই-রঙা। এবং প্রতিটি দরজা-জানালা হাট করে খোলা। সোঁ সোঁ করে হাওয়া বইছে বাড়িগুলোর মধ্যে দিয়ে সমুদ্রপারের মতন অথচ দরজা-জানালাগুলোতে একটুও শব্দ উঠছে না। উঠছে না তা নয়, উঠছে মাঝে মাঝে, রোগীর শেষনিশ্বাসের মতন। আর মনে হচ্ছে কানের কাছে, ঘাড়ের কাছে, কে যেন ডাকছে, ক্রমাগত; ডেকেই যাচ্ছে, আয়! আয়! আয়! কিন্তু কোনো মানুষ নেই। কালো কালো বাড়ি।
গা ছম ছম করে উঠল নরেশবাবুর।
স্বগতোক্তির মতো আবারও শিলিকে বললেন, যমদুয়ার! সে তো মেলাই দূর রে। কী রে শিলি?
–হ! দূর-ই তো! তবে ঠিক কতখানি দূর-তা আমি জানুম কেমনে? মাইয়ারা ত আর শিকারে যায় না।
–তা ঠিক-ই কইছস! কিন্তু মহারানি, রাজকুমারী, ম্যামেরা যায়।
পরেশবাবু বললেন।
অনেক-ই পুরানো কথা মনে পড়ে নরেশবাবুর। দমকে দমকে, বমির মতন অনেক পুরানো কথা বাইরে আসতে লাগল। কত রঙা সব জিনিস তারসঙ্গে। কোথায় যে ছিল তারা এতদিন স্মৃতির কোন কুঠুরির কোন কোণে, ভেবে অবাক হয়ে গেলেন জ্বরক্লিষ্ট নরেশবাবু। শিলি, তার বাবার মুখের দিকে চেয়ে উৎকণ্ঠিত গলাতে বলল, বমি করবা নাকি?
নরেশবাবু বললেন না, না।
মনে মনে বললেন, এই বমি অন্য বমি। তুই বুঝবি না রে ছেমড়ি।
অনেকদিন আগে, পার্টিশনের পরপর-ই একবার তিনিও গেছিলেন যমদুয়ারে শিকারে। হ্যাঁ। তিনিও।
মনে পড়ে গেল।
তবে শিকারি হিসেবে নয়। সঙ্গেই পাউরুটি মাখন আর কলা নিয়ে। ডিমসেদ্ধও। ওই ডিমেই নাকি বিপদ ডেকে এনেছিল। ডিম আর কলা নিয়ে শিকারে গেলেই যাত্রা পন্ড।
কোকরাঝাড়ের গনা ঘোষের একটা বেবি-অস্টিন গাড়ি ছিল। কারখানাও ছিল তাঁর। বলিষ্ঠ দীর্ঘদেহী ধবধবে ফর্সা সাহেবের মতন মানুষ। নীল-রঙা লুঙ্গি পরে, লাল হাফহাতা শার্ট গায়ে দিয়ে একটা মোড়ায় বসে কারখানার তদারকি করতেন। তাঁর কাজে তাঁকে সাহায্য করত তার বড়ো চার ছেলে। ছোটোছেলেও ছিল। আরও পাঁচটি। আর পাঁচমিশেলি বয়সের আটটি মেয়েও। ওঁরা উদবাস্তু নন। কলকাতার হাওড়া জেলার লোক। অদ্ভুত ভাষায় কথা বলতেন। উঠোনকে বলতেন বাকুল। নীচোকে বলতেন নাবো। এইরকম। কত কথাই যে, মনে পড়ে শুয়ে শুয়ে নরেশবাবুর আজকাল। এসব কথা মানুষ যতদিন কর্মঠ থাকে, কাজের মধ্যে থাকে, ততদিন মনে আসে না, নিষ্কর্মা হয়ে গেলেই চৌকির অগণ্য ছারপোকার মতো কুটুস কুটুস কামড়াতে থাকে স্মৃতি, অনুক্ষণ।
সেই গনাবাবু, কলকাতার মনাবাবু, বৈদ্য, আর কে কে যেন ছিল। মনাবাবুর এক বন্ধুও ছিলেন। অজিত সিং। একটা রাইফেল নিয়ে এসেছিলেন তিনি।
মনাবাবুরা কলকাতা থেকে গৌরীপুরে এসেছিলেন। সেখানে সকলে জমায়েত হয়ে এই পথ দিয়েই যমদুয়ারে যাওয়ার সময়ে নরেশবাবুকে তুলে নিয়ে গেছিলেন। শীতকাল ছিল। মনে আছে। আর শীত কী শীত!
জীবনে সেই প্রথম রাইফেল দেখেন নরেশবাবু।
তামাহাট থেকে বড়োবাধা, গুমা রেঞ্জ হয়ে, কচুগাঁও রাইমানা হয়ে যমদুয়ার। যমদুয়ারে পৌঁছোবার আগেই সন্ধে হয়ে গেল আর হাতির পালে ঘিরে ফেলল সেই বেবি-অস্টিন গাড়ি। কী খিটক্যাল! কী খিটক্যাল! যমদুয়ার, সে তত ভারি গহন জঙ্গল। একপাশে বাংলার ডুয়ার্স, অন্যপাশে ভুটান। মধ্যে দিয়ে বয়ে চলেছে সংকোশ নদী। বড়োবাঘ, হাতি, বাইসন, চিতা, কোন জানোয়ার নেই সেখানে?
সংবিৎ ফিরে পেয়ে যেন বললেন পরেশবাবু, কইস কী রে শিলি? যমদুয়ারে গ্যাছে পরেশ?
-হ্যাঁ।
সঙ্গে গেল কেডায় কেডায়?
–ধুবড়ি থিক্যা আইছিল, শিকারিরা। বড়ড়া শিকারি। ভয় নাই তোমার। ছাত্তার চাচায়ও সঙ্গে গেছে। এক সাহেবও আছে নাহি কইতাছিল কাকায়।
-ভয় নাই? কস কী? ভয় তো হের লইগ্যাই। ছাত্তারটা না করতি পারে এমন কাম-ই নাই। তার বাবারেও বাঘে খাইছে। অরেও খাইব। পরেশরে ক্যান যে, এই মরণের নেশায় পাইল! কত নেশাই ত মানষে করে। কিন্তু এ কি গরিবগো ন্যাশা? রাজারাজড়া, জমিদার; যাগো অন্নচিন্তা নাই, তাগো হাই সব মানায়। না করে রোজগার, না করল বিয়া, ইটা কী?
একটু পর-ই বাবা বললেন, দুগা মুড়ি ভাইজা দে দেহি। তেল দিবার লাগব না। আর এট্টু পিয়াজ। কাঁঠালের বিচি ভাইজা দিবি নাহি এটু?
-না না। কাঁঠালের বিচি খাইয়া কাম নাই। এত জ্বর। প্যাটের গোলমাল বাধাইবা আবার জ্বরের উপরে। আমি পড়ম বিপদে।
–যা ভালো বোঝস তুই। তবে, কাল আমার জ্বর ছাইড়া যাইব। মন কইতাছে। এতক্ষণ তো আবারও কম্প দিয়া জ্বর আসনের কথা ছিল। আইল না যহন, তহন, ছাইড়্যাই যাইব গিয়া। এই শৈলেনের ভাই, আমাগো ডাক্তার খুব ভালো। গদাই-এর বাপে তারে যাই-ই কউক না ক্যান!
বাবাকে একটু আদার রস দিয়ে গরম চা আর মুড়ি-ভাজা খাইয়ে, জ্বরটা আর একবার দেখে ক্যাবলাকে বাবার কাছে রেখে, গা ধুয়ে নিল শিলি। তারপর চলল পুতনদাদের বাড়ি। ভাবছে, রাতে একটু সুজির খিচুড়ি বেঁধে দেবে। অথবা সাবুর। কয়েকটা আলু আর পটল ফেলে। আদা-কাঁচালঙ্কা দিয়ে। মসুর ডালের। বাবাকেও দেবে একটু। বুধাই গাইয়ের ঘি তো আছেই। অনেক ঘি খেয়েছে, দুধ খেয়েছে ছোটোবেলা থেকে শিলি। কিন্তু বুধাই-এর দুধের যেমন গন্ধ, তেমনি ঘি-এর। এমন লক্ষ্মী আর মিষ্টি গাই কখনো দেখেনি। তেমন মিষ্টি হয়েছে বাছুরটা।
–পুঁচকি।
নামটা দিয়েছে, শিলিই।
পুতনদাদের বাড়ি বড়োরাস্তা দিয়ে গেল না। সেনদের বাড়ির পাশ দিয়ে আলোকঝারি পাহাড়ের দিকে মুখ করা পথটা ধরল ও।
এই শেষ বিকেলের এই সময়টা বড়োপ্রিয় সময় শিলির। পৃথিবী কেমন যেন, নরম বিবাগি হয়ে যায় এই সময়টাতে। দিনের অন্য সময়ে যা-কিছুই সে নামঞ্জুর করে, গররাজি নারীর মতন, এই সময়ে সেইসব আর্জিও সহজে মঞ্জুর করে দেয়। মৈজুদ্দিন চাচার সন্ধ্যার নামাজের মতো এক বিষণ্ণ সুর বাজে এই শেষ বিকেলের আলোয়। সজনে গাছের ফিনফিনে পাতাদের গায়ে শিহর তুলে উড়ে যায় দুর্গা-টুনটুনি। বাঁশঝাড়ের ছায়ায় ছায়ায় নেংচে হেঁটে যায় মস্ত লম্বা ল্যাজ নিয়ে, ছায়াচ্ছন্ন বনের ছায়া ঝাট দিয়ে; সেই একলা, মস্ত বড়ো বাদামি-কালো পাখিটা।
পরেশকাকু একদিন বলেছিল এর ইংরিজি নাম, ক্রো-ফ্রেজেন্ট। গতবছর। হিতুকাকু আসত প্রায়-ই তামাহাট থেকে। অনেক পাখি আর ফুল চিনত সে। পুতনদাটা চিরদিনই কাঠকাঠ। যেসব ছেলেরা আই-কম-বি-কম পড়ে, তারা বেশিরভাগ-ই ওরকম হয়। কেন, কে জানে? আর যারা খাতা-টাতা লেখে, মুহুরি আর অ্যাকাউন্ট্যান্ট; তারা তো যাচ্ছেতাই। নস্যি নেয়। গোমড়ামুখো। নাকে একটা নিকেলের ফ্রেমের চশমা থাকবেই। কথাবার্তা কারও সঙ্গেই নেই। খালি বলবে; জাবদা, খতিয়ান, হরজাই খাতে, নাজাই খাতে; এইসব।
শিলি এইসব জানে, কারণ শিলির ছোটোমামা মুহুরি ছিলেন। এখন ধুবড়ির এক মহাজনের কাছে কাজ করেন। টাউন স্টোর্স-এর শচীন রায়দের কাছেও কাজ করেছিলেন কিছুদিন। ধুবড়ি শহরে।
শিলি যখন গিয়ে পৌঁছোল, তখন কিরণশশী রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে চালতা মাখছিলেন। শিলিকে দেখেই বললেন, আইছস? তর লইগ্যাই মাখতাছিলাম। তর বাবায় কেমন?
–বাবা এহনে ভালো। মনে হইতাছে জ্বর এক্কেরেই ছাইড়া যাইব গিয়া কাইল-ই সকাল নাগাদ।
–যা তো! রান্নাঘর থিক্যা দুইটা রেকাবি লইয়া আয় ত শিলি।
শিলি, রেকাবি এনে বলল, পিতলের উপর টক গুইব্যা? খারাপ হইয়া যাইব না?
–তুইও য্যামন। তরে পিতলের রেকাবি আনতে কইল কেডায়! পাথরেরডা আন। শিলি, ঘরের ভেতর থেকে বলল, শ্বেতপাথরের, না লালপাথরের না কালাপাথরের? কোন পাথরের? কোন পাথরের আনুম তা ত কইবা?
-নছল্লা থো তো তোর ছেমড়ি! পলকে লইয়া আয়।
শিলি একটু চালতা-মাখা মুখে দিয়েই চোখ-মুখ নাচিয়ে জিভটা টাগরাতে ঠেকিয়ে বলল, উ-উ-উ-উ-ম-ম-ম! বুড়ি তোমার মতন ত কাউরেই দ্যাখলাম না আইজ অবধি। সত্যই কই। চালতা, কাঁচালঙ্কা, এটু লবণ, এটু কাঁচা মরিচ, এটু চিনি আর বেশি কইরা ধইনাপাতা। আহা স্বােয়াদখান কী? য্যান, হাতে চাঁদ পাইছি। এমন স্বোয়াদ পৃথিবীর আর কিছুতেই নাই। কী ভালোই যে, লাগে-না বুড়ি।
কিরণশশী, শিলির অপাপবিদ্ধ মুখের দিকে চেয়ে মনে মনে বললেন, চালতা-মাখার চেয়েও অনেক স্বাদু জিনিস এই পৃথিবীতে আছে। কত কী পাগল-করা অনুভূতি! এমন এমন মুহূর্ত, যখন মনে হয় জীবনের সব শত্রুকে নিঃশর্তে ক্ষমা করে দিই। ও তো জানে না সেসব! জানবে, বিয়ের জল গায়ে পড়লে।
তারপর নিজের মনেই না-বলে বললেন, জীবনভর তো আনন্দই। দুঃখ কতটুকু? এই চালতা-মাখার স্বাদের-ই মতো টক-টক, মিষ্টি-মিষ্টি, ঝাল-ঝাল এই জীবন। জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত।
লোকে জানে, বিধবা, একা, কিরণশশীর অনেক-ই দুঃখ। যারা তা জানে, তারা কিছুই জানে না। সুখ তাঁর চারধারেই ছড়ানো আছে। ঝরাপাতার মতো, মিষ্টি ধুলোর মতো; বাড়ি ফেরা গাইয়ের গায়ের মিষ্টি গন্ধর-ই মতো সুখ ভেসে বেড়াচ্ছে চারপাশে। শুধু তাকে চিনে নেওয়া চাই। মুহূর্তগুলোকে শুধু হারিয়ে যেতে দিতে নেই।
এসব গভীর কথা শিলি কী করে বুঝবে? ও তো ধুলোর মধ্যে ঘর-বানানোর খেলায় মেতে-থাকা চঞ্চল ছটফটে দুরন্ত চড়াই। যে ঘর বানায়নি, ঘরে থাকেনি কখনো, সেই মেয়েই কল্পনার ধুলোয় ঘর বানিয়ে এমন ছটফট করে। ধুলাবাড়ি। বাড়ি নয়। বেচারি জানবেই বা কী করে! এক-একটি করে বছর হারিয়ে, শৈশব-কৈশোর-যৌবন-প্রৌঢ়ত্ব পেরিয়ে পায়ে পায়ে হেঁটে এসে বার্ধক্যে পৌঁছে, জীবনের পেছনে ফেলে-আসা পথের ধুলোয়। মানুষ যা-কিছুই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আসে, হারিয়ে আসে, নিয়েও আসে; তার নাম-ই তো জীবন। অভিজ্ঞতার আর এক নাম-ই জীবন। যা বয়স হারিয়ে পাওয়া যায়, তা কি বয়স না-হারিয়ে কখনোই পাওয়া যায়?
শিলিকে বসিয়ে, রান্নাঘরের দাওয়ায় পা-ঝুলিয়ে বসে চালতা-মাখা খাওয়া শিলির খুশিমুখের দিয়ে চেয়ে, ক্ষণিকের জন্যে নিজের প্রথম যৌবনে ফিরে যান কিরণশশী। শিলির বয়সে। তাঁর ফোকলা মুখে হাসি ফুটে ওঠে। কুঁচকে-যাওয়া, কালিপড়া চোখ দু-খানিতে এক প্রসন্ন কৌতুক ভোরের প্রথম আলো-পড়া শিশিরবিন্দুর মতো ঝিকমিক করে ওঠে।
শিলি মুখ ঘুরিয়ে, কনে-দেখা আলোয় কিরণশশীর মুখের হাসি দেখে। প্রথমে অবাক হয়। তারপর গম্ভীর হয়ে যায়। পরক্ষণেই নিজেও হেসে ফেলে।
বলে, মরণ। হাসো ক্যান মিটমিটাইয়া? ও বুড়ি?
বুড়ি আবারও হাসেন।
–আরে! কইবা তো! এত হাসনের হইলডা কী?
–তরে দেহি আর হাসি।
–না। হাসবা না। কইয়া দিলাম।
–ক্যান? হাসির উপরও ট্যাক্সো চাপছে নাকি?
তারপর দু-জনেই আবার হেসে ওঠে।
হাসতে হাসতে, শিলির আঁচল লুটিয়ে পড়ে বারান্দার দাওয়ায়।
এমন করে আগল খুলে, নিভৃতে দু-জন নারীই শুধু হাসতে পারে।
উঠোনের কোনা অবধি এগিয়ে-আসা একটা কাঠবেড়ালি হাসির শব্দে ভয় পেয়ে তরতরিয়ে সুপুরি গাছের ওপরে উঠে যায়। গাছের অনেকখানি ওপরে উঠে, ল্যাজ তুলে তুলে শিহরভরে ডাকে, চিহর-চিহর-চিরিপ-চিরিপ-চিরিপ। আর ঠিক সেই সময়ই গৌরীপুর থেকে আসা বিকেলের বাসটা তামাহাটের দিকে চলে যায় পক পক করে বালব-হর্ন বাজিয়ে।
সন্ধে হল।
পুতনদাদাদের বাড়ির মোতি গাই ডাকে গোয়ালঘর থেকে, হাম্বা-আ-আ-আ। লিচু গাছের ডাল ছেড়ে বাদুড়েরা পা-আলগা করে ভেসে যায়। অন্ধকারে মিশে যায় তাদের ডানার সপ সপ সপ সপ শব্দ।
রমজান মিয়ার ছোটো ছাওয়ালটা সারাদিন শুকিয়ে-যাওয়া চৈত্রের পুকুরে পোলো দিয়ে দিয়ে কই-শিঙি মাছ ধরে। দিনশেষে আব্বাসউদ্দিনের গান গাইতে গাইতে পুতনদের বাড়ির দিকে আসতে থাকে। গলা ছেড়ে গান গায় সে: বগা কান্দেরে, তোরসানদীর পারে পারে, ফানদে পইড়্যা বগা কান্দেরে…
চৈত্রশেষের সন্ধ্যার কাঁসা-রঙা আলোয়, শ্যাওড়া গাছের গন্ধ, বাছুরের গায়ের গন্ধ, হাসনুহানার গন্ধ, সদ্য-চেরাই-করা হরজাই কাঠের মিষ্টি গন্ধের মধ্যে, গা-মাথাময় পুকুরের পুরোনো কাদা আর শামুক-গুগলির, কই-শিঙির আর গুঁড়িগুঁড়ি শ্যাওলার গন্ধ গায়ে মেখে আলিমুদ্দিন এসে দাঁড়ায় উঠোনে।
বলে, ফুফা, একখান সানকি দাও দেহি। শিলিদিদিরে মাছ দিয়া যাই কয়খান।
শিলি হাসে।
বলে, খুব যে পেরেম দেহি রে ছ্যামড়া। কাইলকা হক্কালে আইস্যা, টাহা কয়ডা চাইবি তা ক দেহি আগে?
আলিমুদ্দিন হাসে।
মিষ্টি ছেলেটা। বলে, টাহাই কি দুনিয়ায় সব শিলিদিদি? তুমি একবার হাইস্যা দিয়ে তাইলেই হইব। দাম নিমু না। পেরেমটা চিনলা না, টাহাই চিনলা শুধু! তোমার কপালে পেরেম লাই।
-তবে রে ছ্যামড়া।
কপট-ক্রোধে শিলি তেড়ে যায় আলিমুদ্দিনের দিকে।
হাসতে হাসতে, কপট ভয়ে, আলিমুদ্দিন পিছিয়ে যায়।
মাছ ঢেলে দিতে দিতে বলে, দাম নিমু না। হত্যই কইতাছি শিলিদিদি। একদিন আইমু অনে পুতনদা আইলে পর। গান শুনাইও দিদি একখান, পূর্ণিমার রাতে, বারান্দায় বইস্যা। আহা! গান তো গাও না তুমি, মনে হয় গঙ্গাধারে পূর্ণিমার রাইতে পাল তুইল্যা নৌকা ভাইস্যা যাইতাছে গিয়া। পরাণের মধ্যেটা কেমন কেমন করে য্যান।
শিলি আর কিরণশশী বলেন, যাত্রায় পার্ট করস না ক্যান তুই? গান তুইও তো খারাপ গাস না রে ছ্যামড়া।
আলিমুদ্দিন হাসে। বলে, মোক নেয় কেডায়, তাই কও। আলিমুদ্দিন তোমাদের গান শুনাইতে পারলেই সুখী। আর কিসুর লোভ নাই।
তারপরে বলে, গান তো গায় ফুফা সব পাখিতেই। কোকিল কি সবাই হইতে পারে? কও দেহি? আমাগো শিলিদিদি হইতাছে কুমারগঞ্জের কোকিল।
-হইছে। ফাইজলামি রাইখ্যা এহন বাড়ি যাইয়া ধোয়াপাকলা কইরা চান কইর্যা ফ্যালা। রাত হইয়া গেল। এতক্ষণ, কী মাছ ধরতাছিলি তুই?
–হঃ। হুদাই মাছ? এক-একবার পোলো ফ্যালাই, পোলোর মধ্যে হাতাটরে ফেরাই আর কত কী ভাবি! ভাবি, আমার বেহেস্ত আর দোজখ দুই-ই আছে এই পোলোর মধ্যেই। কোনটারে ফ্যালাই আর কোনটারে উঠাই? বাস এই করতা করতাই দিল এক ব্যাটা সাপে কামড় দিয়া।
–সাপ?
শিলি চমকে উঠল।
-তারপর?
কিরণশশী বললেন।
–কী সাপ?
শিলি উৎকণ্ঠিত হয়ে শুধোল।
কিরণশশী আবার বললেন, তারপর?
-তারপর আর কী? দোজখে যে, হাত দিছি বোঝাই গেল তা। বলেই, ফুলে-যাওয়া হাতটা তুলে দেখিয়ে বলল, ত্যামন সাপ হইলে তো কাম-ই সারত যাইত গিয়া এতক্ষণে।
তারপর স্বগতোক্তির মতন বলল, জল-ঢোঁড়াই হইব।
বলেই বলল, মাছগুলান লইয়া লও ফুফা। যামু এবার। কাদায় চিড়বিড় করতাছে গা।
সাবধানে যাইসানে ভাইডি। বাঁশবাগানের তলায়ও একজোড়া গোখরার বাসা আছে। জানস তো?
-জানি জানি। বুকের মধ্যে কত গোখরার ছোবল খাই, গোখরারে আমি ডরাই না।
–বুকের মধ্যে ছোবল? হেডা আবার কী?
শিলি বলল, অবাক হয়ে।
–ক্যান। তোমার হাসি।
আলিমুদ্দিন বলল।
–এইবার আমি তরে মারুম। পালা। যাইবি কি না ক তুই।
–যাইতাছি। এই পলাইলাম।
বলেই, আলিমুদ্দিন আধো-অন্ধকারে কাদা-মাখা একটি মস্ত ভোঁদড়ের মতো দু-পায়ে থপথপ করে চলে গেল।
শিলি গলা তুলে বলল, যাওন নাই রে, আসিস আলিম ভাই আবার।
–আ-সুম।
গলা তুলে বলল, আলিমুদ্দিন দূর থেকে।
তার গলার আওয়াজকে, লটকাগাছের ঝুপরি পাতাগুলো অন্ধকারে কপাৎ করে গিলে ফেলল।
ওদের চালতা খাওয়া হয়ে গেছে। হোন্দলের মা এতক্ষণ হ্যারিকেন আর রান্নাঘরের লক্ষ পরিষ্কার করছিল। সব ঘরের বারান্দায়, ছাই দিয়ে কাচ মেজে, ঝকঝকে করে, হ্যারিকেন রেখে গেল।
শিলি বলল, গাছের ছায়াঘেরা মিটমিটে আলোতে ঘন হয়ে ওঠে উঠোনভরতি অন্ধকারে, লজ্জা লজ্জা গলায়; পুতনদার চিঠি কি আইছে? বুড়ি?
–নাঃ
কিরণশশীর দীর্ঘশ্বাস চাপা এই না-টা অন্ধকার তারাভরা আকাশের দিকে দু-টি নারীর চারটি উঁচু-করা প্রতিবাদের হাতের মতো বলে উঠল না, না, না।
দু-জনের মনেই কু-ডাক দিল। নীরবেই মনে মনে দু-জনে বলল, দু-জনের মতো করে, ও আসবে–না, ও আর আসবে না ফিরে। তাই-ই চিঠি লেখে না ও!
কিরণশশী বললেন, শিলিকে কাকুতি করে, তুই লিখছিলি কি অরে?
-হ।
কবে?
–গতমাসে।
–গতমাসে। তারপর আর একবার লিখতে কী হইছিল? আঙুলে কি বাত ধরছে তর?
–তা না। তোমার পোলারে তুমিই লিখবা। আমি ক্যান বারে বারে লিখুম? জবাব যে, দ্যায় না, তারে লিখুম-ই বা ক্যান? স্যা আমার কেডা?
কিরণশশী কিছু না বলে, চুপ করে বাড়ির পশ্চিমে চেয়ে রইলেন।
আকাশে তখনও ফিকে গোলাপি আভা ছিল সামান্য। একঝাঁক সল্লিহাঁস কোনাকুনি উড়ে গেল। অন্ধকার নেমে এল ঝুপ করে। আলোর সামান্যতম আভাসও আর রইল না।
শিলি উঠল। বলল, যাই বুড়ি।
কিরণশশী বিড় বিড় করে, শীতের দীর্ঘরাতের আগুনের মতন বলল, যাওন নাই মাইয়া। আইস্যো।