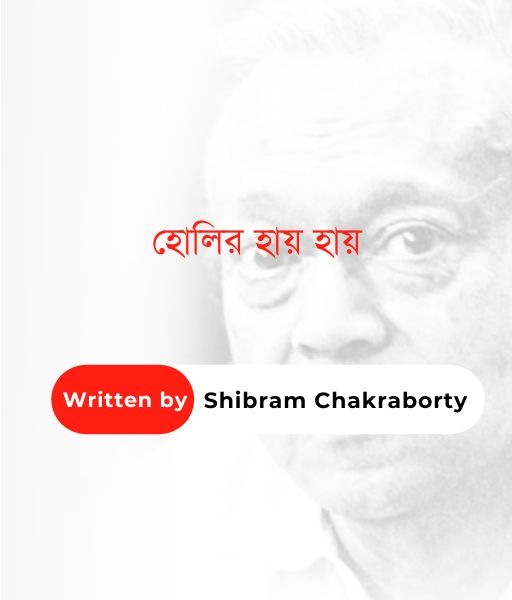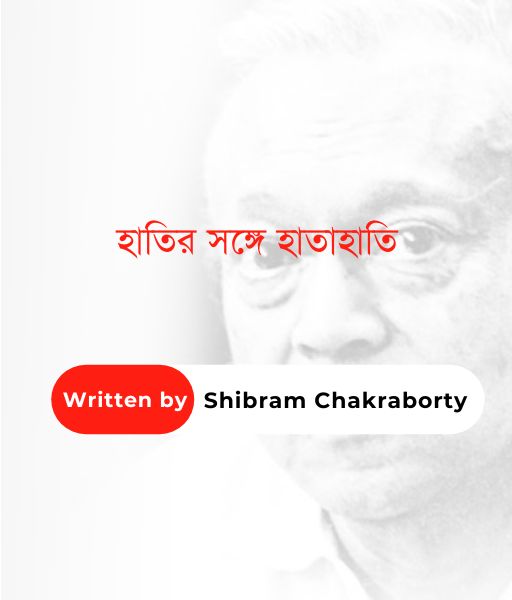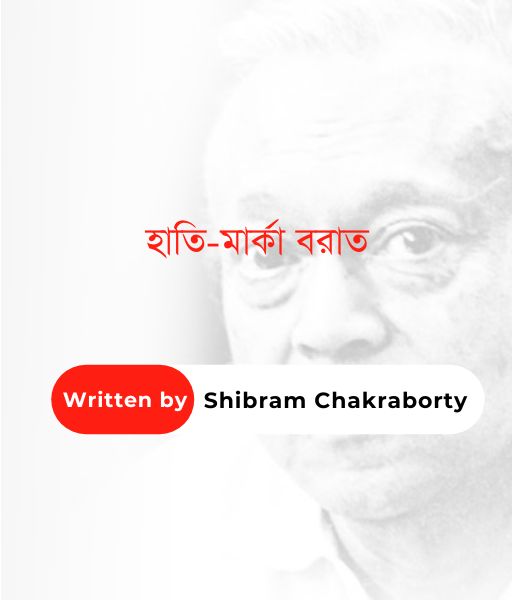আমার সম্পাদক শিকার
হাম কিংবা টাইফয়েড, সর্পাঘাত কিংবা মোটরচাপা, জলে-ডোবা কিংবা গাছ থেকে পড়ে যাওয়া, এগজামিনে ফেল-করা কিংবা কাঁকড়াবিছে কামড়ানো—জন্মাবার পর এর কোনোটা-না-কোনোটা কারও-না-কারও বরাতে কখনো-না-কখনো একবার ঘটেই। অবশ্য যে মোটর চাপা পড়ে তার সর্পাঘাত হওয়া খুব শক্ত ব্যাপার, সেরকম আশঙ্কা প্রায় নেই বললেই হয়, এবং যার সর্পাঘাত হয় তাকে আর গাছ থেকে পড়তে হয় না। যে ব্যক্তি জলে ডুবে যায় মোটর চাপা পড়ার সুযোগ তার যৎসামান্যই এবং উঁচু দেখে গাছ থেকে ভালো করে পড়তে পারলে তার আর জলে ডোবার ভয় থাকে না। তবে কাঁকড়াবিছের কামড়ের পরেও এগজামিনে ফেল করা সম্ভব, এবং অনেকক্ষেত্রে হামের ধাক্কা সামলাবার পরেও টাইফয়েড হতে দেখা গেছে। হামেশাই দেখা যায়।
কিন্তু বলেছিই, এসব কারও-না-কারও অদৃষ্টে ঘটে কখনো বা কদাচ। কিন্তু একটা দুর্ঘটনা প্রায় সবারই জীবনে একটা নির্দিষ্ট সময়ে অনিবার্যরূপে প্রকট হয়, তার ব্যতিক্রম খুব বড়ো একটা দেখা যায় না। আমি গোঁফ ওঠার কথা বলছিনে—তার চেয়ে শক্ত ব্যারাম—গোঁফ ওঠার সঙ্গে সঙ্গে লেখক হবার প্রেরণা মানুষকে পেয়ে বসে।
আমারও তাই হয়েছিল। প্রথম গল্প লেখার সূত্রপাতেই আমার ধারণা হয়ে গেল আমি দোলগোবিন্দবাবুর মতো লিখতে পেরেছি। দোলগোবিন্দকে আমি রবীন্দ্রনাথের সমকক্ষ মনে করতাম—কেননা একই কাগজে দুজনের নাম একই টাইপে ছাপার অক্ষরে দেখেছিলাম আমি। এমনকী অনেকসময় দোলগোবিন্দকে রবীন্দ্রনাথের চেয়েও বড়ো লেখক আমার বিবেচনা হয়েছে—তাঁর লেখা কেমন জলের মতো বোঝা যায়, অথচ বোঝার মতন মাথায় চাপে না! কেন যে তিনি নোবেল প্রাইজের জন্য চেষ্টা করেন না, সেই গোঁফ ওঠার প্রাক্কালে অনেক বার আমি আন্দোলন করেছি—অবশ্যি মনে মনে। এখন বুঝতে পারছি পন্ডিচেরি, কিংবা পাশাপাশি, রাঁচিতে তাঁকে পরামর্শ দেবার কেউ ছিল না বলেই। আরও দুঃখের বিষয়, রবীন্দ্রনাথের লেখা এখনও চোখে পড়ে থাকে কিন্তু কোনো কাগজপত্রেই দোলগোবিন্দবাবুর দেখা আর পাই না।
যা-ই হোক, গল্পটা লিখেই বাংলাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ মাসিকপত্রে, দোলগোবিন্দ বা রবীন্দ্রনাথের রচনার ঠিক পাশেই সেটা প্রকাশ করার জন্য পাঠিয়ে দিলাম। নিশ্চিন্তে বসে আছি যে নিশ্চয়ই ছাপা হবে এবং ছাপার অক্ষরে লেখাটা দেখে কেবল আমি কেন, রবীন্দ্রনাথ, এমনকী, স্বয়ং দোলগোবিন্দ পর্যন্ত পুলকিত হয়ে উঠবেন—ও হরি! পর পর তিন মাস হতাশ হবার পরে একদিন দেখি বুকপোস্টের ছদ্মবেশে লেখাটা আমার কাছেই আবার ফিরে এসেছে। ভারি মর্মাহত হলাম বলাই বাহুল্য! শোচনীয়তা আরও বেশি এইজন্য যে তিন মাসে তিনখানা কাগজ কিনেছিলাম—খতিয়ে দেখলাম সেই দেড়টা টাকাই ব্যাটাদের লাভ!
তারপর, একে একে আর যে-কটা নামজাদা মাসিক ছিল সবাইকে যাচাই করা হল—কিন্তু ফল একই। আট আনার পেটমোটাদের ছেড়ে ছ-আনার কাগজদের ধরলাম—অবশেষে চার আনা দামের নব্যপন্থীদেরও বাজিয়ে দেখা গেল। না:, সব শেয়ালের একই রা! হ্যাঁ, গল্পটা ভালোই, তবে ছাপতে তাঁরা অক্ষম! আরে বাপ, এত অক্ষমতা যে কেন তা তো আমি বুঝতে পারিনে, যখন এত লেখাই অনায়াসে ছাপতে পারছ তোমরা! মাসিক থেকে পাক্ষিক—পাক্ষিক থেকে সাপ্তাহিকে নামলাম; অগত্যা লেখাটার দারুণ অমর্যাদা ঘটছে জেনেও দৈনিক সংবাদপত্রেই প্রকাশের জন্য পাঠালাম। কিন্তু সেখান থেকেও ফেরত এল। দৈনিকে নাকি এত বড়ো ‘সংবাদ’ ধরবার জায়গাই নেই। আশ্চর্য! এত আজেবাজে বিজ্ঞাপন—যা কেউ পড়ে না তার জন্য জায়গা আছে, আমার বেলাই যত স্থানাভাব? বিজ্ঞাপন বাদ দিয়ে ছাপলেই তো হয়। কিন্তু অদ্ভুত এঁদের একগুঁয়েমি—সব সংবাদপত্র থেকেই বারংবার সেই একই দুসংবাদ পাওয়া গেল।
তখন বিরক্ত হয়ে, শহর ছেড়ে মফসসলের দিকে লক্ষ দিতে হল—অর্থাৎ লেখাটা দিগবিদিক পাঠাতে শুরু করলাম। মেদিনীপুর-মন্থন, চুঁচুড়া-চন্দ্রিকা, বঁাকুড়া হরকরা, ফরিদপুর-সমাচার, গৌহাটি-গবাক্ষ, মালদহের গৌড়বান্ধব কারুকেই বাদ রাখলাম না। কিন্তু শহুরে পেটমোটাদের কাছ থেকে যে দুর্ব্যবহার পাওয়া গেছে, পাড়াগেঁয়ে ছিটেফোঁটাদের কাছেও তার রকমফের হল না। আমার বিরুদ্ধে দেশব্যাপী এক দারুণ ষড়যন্ত্র আমার সন্দেহ হতে লাগল।
এইভাবে সেই প্রথম ও পুরোবর্তী লেখার ওপরে ‘ট্রাই অ্যাণ্ড ট্রাই এগেন’ পলিসির কার্যকারিতা পরীক্ষা করতেই বাংলা মুলুকের তাবৎ কাগজ আর সাড়ে তিন বছর গড়িয়ে গেল—বাকি রইল কেবল একখানি কাগজ—কৃষি সম্বন্ধীয় সাপ্তাহিক। চাষাড়ে কাগজ বলেই ওর দিকে এতাবৎ আমি মনোযোগ দিইনি, তারা কি আমার এই সাহিত্য রচনার মূল্য বুঝবে? ফেরত তো দেবেই, হয়তো সঙ্গে সঙ্গে বলে পাঠাবে, ‘মশাই, আপনার আষাড়ে গল্প আমাদের কাগজে অচল; তার চেয়ে ফুলকপির চাষ সম্বন্ধে যদি আপনার কোনো বক্তব্য থাকে তা লিখে পাঠালে বরং আমরা চেষ্টা করে দেখতে পারি।’
এই ভয়েই এতদিন ওধারে তাকাইনি—কিন্তু এখন আর আমার ভয় কী? (ডুবন্ত লোক কি কুটো ধরতে ভয় করে?) কিন্তু না; ওদের কাছে আর ডাকে পাঠানো নয়, অনেক ডাকখরচা গেছে অ্যাদ্দিন, এবার লেখা সমভিব্যাহারে আমি নিজেই যাব।
‘দেখুন, আপনি—আপনিই সম্পাদক, না? আমি—আমি একটা—একটা লেখা এনেছিলাম আমি—’ উক্ত সম্পাদকের সামনে হাজির হয়ে হাঁক পাড়লাম।
গম্ভীর ভদ্রলোক চশমার ফাঁকে কটাক্ষ করলেন—‘কই দেখি!’
‘একটা গল্প। একেবারে নতুন ধরনের—আপনি পড়লেই বুঝতে পারবেন।’ লেখাটা বাড়িয়ে দিলাম ‘আনকোরা প্লটে আনকোরা স্টাইলে একেবারে—’
ভদ্রলোক গল্পে মনোযোগ দিয়েছেন দেখে আমি বাক্যযোগ স্থগিত রাখলাম। একটু পড়তেই সম্পাদকের কপাল কুঞ্চিত হল, তারপরে ঠোঁট বেঁকে গেল, নাক সিঁটকাল, দাড়িতে হাত পড়ল,—যতই তিনি এগুতে লাগলেন, ততই তাঁর চোখ-মুখের চেহারা বদলাতে লাগল, অবশেষে পড়া শেষ করে যখন তিনি আমার দিকে তাকালেন তখন মনে হল তিনি যেন হতভম্ব হয়ে গেলেন। হতেই হবে। কীরকম লেখা একখান!
‘হ্যাঁ, পড়ে দেখলাম—নিতান্ত মন্দ হয়নি! তবে এটা যে একটা গল্প তা জানা গেল আপনি গল্পের নামের পাশে ব্র্যাকেটের মধ্যে কথাটা লিখে দিয়েছেন বলে—নতুবা বোঝার আর কোনো উপায় ছিল না।’
‘তা বটে। আপনারা সম্পাদকরা যদি ছাপেন তবেই নতুন লেখক আমরা উৎসাহ পাই।’ বলতে বলতে আমি গলে গেলাম, ‘এ গল্পটা আপনার ভালো লেগেছে তাহলে?’
‘লেগেছে একরকম। তা এটা কি—’
‘হ্যাঁ, অনায়াসে। আপনার কাগজের জন্যেই তো এনেছি।’
‘আমার কাগজের জন্য?’ ভদ্রলোক বসেই ছিলেন কিন্তু মনে হল যেন আরও একটু বসে গেলেন, ‘তা আপনি কি এর আগে আর কখনো লিখেছেন?’
ঈষৎ গর্বের সঙ্গেই আমি জবাব দিলাম, ‘না:, এই আমার প্রথম চেষ্টা।’
‘প্রথম চেষ্টা? বটে?’ ভদ্রলোক ঢোঁক গিললেন, ‘আপনার ঘড়িতে ক-টা এখন?’
ঘড়িটা পকেট থেকে বার করে অপ্রস্তুত হলাম, মনে পড়ল কদিন থেকেই এটা বন্ধ যাচ্ছে, অথচ ঘড়ির দোকানে দেওয়ার অবকাশ ঘটেনি। সত্য কথা বলতে কী, সম্পাদকের কাছে ঘড়ি না হোক, অন্তত ঘড়ির চিহ্নমাত্র না নিয়ে যাওয়াটা ‘বে-স্টাইলি’ হবে ভেবেই আজ পর্যন্ত ওটা সারাতে দিইনি। এখান থেকে বেরিয়েই বরাবর ঘড়ির দোকানে যাব এই মতলব ছিল।
ঘড়িটাকে ঝাঁকুনি দিয়ে বললাম, ‘না: বন্ধ হয়ে গেছে দেখছি। কদিন থেকেই মাঝে মাঝে বন্ধ যাচ্ছে।’
‘তাই নাকি? দেখি তো একবার?’ তিনি হাত বাড়ালেন।
‘ঘড়ি মেরামতও জানেন নাকি আপনি?’ আমি সম্ভ্রমভরে উচ্চারণ করলাম।
‘জানি বলেই তো মনে হয়। কই দেখি, চালানো যায় কি না।’
আমি আগ্রহভরে ঘড়িটা ওঁর হাতে দিলাম—যদি নিখরচায় লেখা আর ঘড়ি একসঙ্গে চালিয়ে নেওয়া যায়, মন্দ কী!
ভদ্রলোক পকেট থেকে পেনসিল-কাটা ছুরি বার করলেন; তার একটা চাড় দিতেই পেছনের ডালার সবটা সটান উঠে এল। আমি চমকে উঠতেই তিনি সান্ত্বনা দিলেন, ‘ভয় কী? জুড়ে দেব আবার।’
সেই ভোঁতা ছুরি এবং সময়ে সময়ে একটা চোখা কলমের সাহায্যে তিনি একটার পর একটা ঘড়ির সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ খুলে ফেলতে লাগলেন। মিনিট এবং সেকেণ্ডের কাঁটাও বাদ গেল না। খুঁটিনাটি যত যন্ত্রপাতি টেবিলের উপর স্তূপাকার হল—তিনি এক-একটাকে চশমার কাছে এনে গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করছিলেন। সূক্ষ্ম তারের ঘোরানো ঘোরানো কী একটা জালের মতো—বোধ হয় হেয়ার-স্প্রিংই হবে—দু-হাতে ধরে সেটাকে লম্বা করার চেষ্টা করলেন। দেখতে দেখতে সেটা দুখান হয়ে গেল, মৃদু হাস্য করে আমার দিকে তাকালেন; তার মানে, ভয় কী, আবার জুড়ে দেব।
ভয় ছিল না কিন্তু ভরসাও যেন ক্রমশ কমে আসছিল। যেটা জুয়েলের মধ্যে সবচেয়ে স্থূলকায় সেটাকে এবার তিনি দাঁতের মধ্যে চাপলেন, দাঁত বসে কি না দেখবার জন্যই হয়তো বা। কিন্তু দন্তস্ফুট করতে না পেরে সেটাকে ছেড়ে ঘড়ির মাথার দিকের দম দেবার গোলাকার চাবিটাকে মুখের মধ্যে পুরলেন তারপর। একটু পরেই কটাস করে উঠল; ওটার মেরামত সমাধা হয়েছে বুঝতে পারলাম।
তারপর সমস্ত টুকরোটাকরা এক করে ঘড়ির অন্তঃপুরে রেখে তলাকার ডালাটা চেপে বন্ধ করতে গেলেন; কিন্তু ডালা তাতে বসবে কেন? সেউঁচু হয়ে রইল। ওপরের ডালাটা আগেই ভেঙেছিল, এবার সেটাকে হাতে নিয়ে আমাকে বললেন, আঠার পাত্রটা আগিয়ে দিন তো—দেখি এটাকে!’
অত্যন্ত নিরুৎসাহে গামের শিশিটা বাড়িয়ে দিলাম। তিনি আঠার সহায়তায় যথেষ্ট সংগ্রাম করলেন কিন্তু তাঁর যৎপরোনাস্তি চেষ্টা সমস্ত ব্যর্থ হল। আঠায় কখনো ও-জিনিস সাঁটানো যায়? তখন সবগুলো মুঠোয় করে নিয়ে আমার দিকে প্রসারিত করলেন—‘এই নিন আপনার ঘড়ি।’
আমি অবাক হয়ে এতক্ষণ দেখছিলাম, বললাম—‘এ কী হল মশাই?’
তিনি শান্ত কন্ঠে জবাব দিলেন—‘কেন, মেরামত করে দিয়েছি তো!’
বাবার কাছ থেকে বাগানো দামি ঘড়িটার এই দফারফা দেখে আমার মেজাজ গরম হয়ে গেল—‘এই বুঝি মেরামত করা? আপনি ঘড়ির যদি কিছু জানেন না তবে হাত দিতে গেলেন কেন?’
‘কেন, কী ক্ষতি হয়েছে?’ একথা বলে তিনি অনায়াসে হাসতে পারলেন—‘তা ছাড়া, আমারও এই প্রথম চেষ্টা।’
আমি অনেকক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে রইলাম, তারপর বললাম, ‘ওঃ! আমার প্রথম লেখা বলেই এটা আপনার পছন্দ হয়নি? তা-ই বললেই পারতেন—ঘড়ি ভেঙে একথা বলা কেন?’ আমার চোখ ফেটে জল বেরোবার মতো হল, কিন্তু অবাঞ্ছিত অশ্রু কোনোমতে সংবরণ করে, এমনকী অনেকটা আপ্যায়িতের মতো হেসেই অবশেষে বললাম—‘কাল নাহয় আর একটা নতুন গল্প লিখে আনব, সেটা আপনার পছন্দ হবে। চেষ্টা করলেই আমি লিখতে পারি।’
‘বেশ আসবেন।’ এ বিষয়ে সম্পাদকের বিশেষ উৎসাহ দেখা গেল, ‘কিন্তু ওই সঙ্গে আর একটা নতুন ঘড়িও আনবেন মনে করে। আমাদের দুজনেরই শিক্ষা হবে তাতে। আপনারও লেখার হাত পাকবে, আমিও ঘড়ি সম্বন্ধে পরিপক্কতা লাভ করব।’
পরের দিন ‘মরিয়া’ হয়েই গেলাম এবং ‘ঘড়িয়া’ না হয়েই। এবার আর গল্প না, তিনটে ছোটো ছোটো কবিতা—শিম, বেগুন, বরবটির উপরে।
আমাকে দেখেই সম্পাদক অভ্যর্থনা করলেন—‘এই যে এসেছেন, বেশ। ঘড়ি আছে তো সঙ্গে?’
আমি দমলাম না—‘দেখুন এবারে একেবারে অন্য ধরনের লিখেছি। লেখাগুলো সময়োপযোগী, এমনকী সবসময়ের উপযোগী। এবং যদি অনুমতি করেন তাহলে একথাও বলতে সাহস করি যে আপনাদের কাগজের উপযুক্তও বটে। আপনি যদি অনুগ্রহ—’
আরও খানিকটা মুখস্থ করে আনা ছিল কিন্তু ভদ্রলোক আমার আবৃত্তিতে বাধা দিলেন—‘ধৈর্য, উৎসাহ, তিতিক্ষা এসব আপনার আছে দেখছি। পারবেন আপনি। কিন্তু আমাদের মুশকিল কী জানেন, বড়ো লেখকেরই বড়ো লেখা কেবল আমরা ছাপতে পারি। প্রবন্ধের শেষে বা তলার দিকে দেওয়া চলে এমন ছোটোখাটো খুচরোখাচরা যদি আপনার কিছু থাকে তাহলে বরং—। এই ধরুন, চার লাইনের কবিতা কিংবা কৌতুক-কণা—’
আমি তাঁর মুখের কথা কেড়ে নিলাম—‘হ্যাঁ, কবিতা। কবিতাই এনেছি এবার। পড়ে দেখুন আপনি, রবীন্দ্রনাথের পরে এমন কবিতা কেউ লিখেছে কি না সন্দেহ।’
তিনি কবিতা তিন পিস হাতে নিলেন এবং পড়তে শুরু করে দিলেন—
‘শিম।
শিমের মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর।
ধামার মাঝে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর।।’
সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সপ্রশংস অভিব্যক্তি দেখা গেল—‘বা:, বেড়ে হয়েছে। আপনি বুঝি শিমের ভক্ত? শিম খেয়ে থাকেন খুব? অত্যন্ত ভালো জিনিস, যথেষ্ট ভিটামিন।’
‘শিম আমি খাইনে। বরং অখাদ্যই মনে করি। তবে এই কবিতাটা লিখতে হিমসিম খেয়েছি।’
‘হ্যাঁ, এগুলো চলবে। খাসা কবিতা লেখেন আপনি; বরবটির সঙ্গে চটপটির মিলটা মন্দ না। তুলনাটাও ভালো—তা, এক কাজ করলে তো হয়!’—অকস্মাৎ তিনি যেন গভীর চিন্তায় আচ্ছন্ন হলেন। ‘দেখুন, ভিটামিনের কাগজ বটে কিন্তু ভিটামিন আমরা খুব কমই খাই। কলা বাদ দিয়ে কলার খোসা কিংবা শাঁস বাদ দিয়ে আলুর খোসার সারাংশ প্রায়ই খাওয়া হয়ে ওঠে না—এইজন্যে মাস কয়েক থেকে বেরিবেরিতে ভুগতে হচ্ছে; তা আপনি যদি—’ তিনি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন।
‘হ্যাঁ, পারব। খুব পারব। ঝুড়ি ঝুড়ি কলার খোসা আপনাকে জোগাড় করে দেব। কিন্তু শুধু খোসা তো কিনতে পাওয়া যায় না, কলার দামটা আপনিই দেবেন।’ তাঁর সমর্থনের অপেক্ষায় একটু থামলাম, ‘কলাগুলো আমিই নাহয় খাব কষ্টেসৃষ্টে—যদিও অনুপকারী, তবু বেরিবেরি না হওয়া পর্যন্ত খেতে তো কোনো বাধা নেই?’
‘না, সেকথা নয়। আমি বলছি কী, আমি তিন মাসের ছুটি নিয়ে ঘাটশিলায় হাওয়া বদলাতে যেতাম, আপনি যদি সেই সময়ে আমার কাগজটা চালাতেন।’
‘আমি?’ এবার আমি আকাশ থেকে পড়লাম যেন।
‘তা, লিখতে না জানলেও কাগজ চালানো যায়। লেখক হওয়ার চেয়ে সম্পাদক হওয়া সোজা। আপনার সঙ্গে আমার এই চুক্তি থাকবে—আপনাকে নামজাদা লেখকদের তালিকা দিয়ে যাব, তাঁদের লেখা আপনি চোখ বুজে চালিয়ে দেবেন—কেবল কপি মিলিয়ে প্রুফ দেখে দিলেই হল। সেইসব লেখার শেষে পাতার তলায় তলায় যা এক-আধটু জায়গা পড়ে থাকবে সেখানে আপনার এই ধরনের ছোটো ছোটো কবিতা আপনি ছাপতে পারবেন, তাতে আমার আপত্তি নেই। এইরকম কৃষি-কবিতা—ওলকপি, গোলআলু, শকরকন্দ—যার সম্বন্ধে খুশি লিখতে পারেন।’
বলা বাহুল্য, আমাকে রাজি করতে ভদ্রলোককে মোটেই বেগ পেতে হল না, সহজেই আমি সম্মত হলাম। এ যেন আমার হাতে স্বর্গ পাওয়া—গাছে না উঠতেই এক কাঁদি। সম্পাদক শিকার করতে এসে সম্পাদকতা-স্বীকার—তোমাদের মধ্যে খুব কম অজাতশ্মশ্রু লেখকেরই এরকম সৌভাগ্য হয়েছে বলে আমার মনে হয়।
সম্পাদনা-কাজের গোড়াতেই এক জোড়া চশমা কিনে ফেললাম; ফাউন্টেন পেন তো ছিলই। অতঃপর সমস্ত জিনিসটাই পরিপাটিরকম নিখুঁত হল। কলম বাগিয়ে ‘কৃষিতত্ত্বের’ সম্পাদকীয় লিখতে শুরু করলাম। যদিও সম্পাদকীয় লেখার জন্য ঘুণাক্ষরেও কোনো অনুরোধ ছিল না সম্পাদকের, কিন্তু ওটা বাদ দিলে সম্পাদকতা করার কোনো মানেই হয় না, আমার মতে। অতএব লিখলাম।
‘আমাদের দেশে ভদ্রলোকদের মধ্যে কৃষি সম্বন্ধে দারুণ অজ্ঞতা দেখা যায়। এমনকী, অনেকের এরকম ধারণা আছে যে, দরজা, জানালা, কড়িবরগা, পেনসিল, তক্তপোশে যেসব কাঠ সাধারণত দেখতে পাওয়া যায় সে-সমস্ত ধান গাছের। এটা অতীব শোচনীয়। তাঁরা শুনলে অবাক হয়ে যাবেন যে ওগুলো ধান গাছের তো নয়ই, বরঞ্চ পাট গাছের বলা যেতে পারে। অবশ্য পাট গাছ ছাড়াও কাঠ জন্মায়; আম, জাম, কাঁঠাল, কদবেল ইত্যাদি বৃক্ষেরাও তক্তাদান করে থাকে। কিন্তু নৌকার পাটাতনে যে-কাঠ ব্যবহৃত হয় তা কেবলমাত্র পাটের।…
ইত্যাদি—এইভাবে একটানা প্রায় আড়াই পাতা কৃষি-তত্ত্ব। কাগজ বেরোতে না বেরোতে আমার সম্পাদকতার ফল প্রত্যক্ষ করা গেল। মোটে পাঁচশো করে আমাদের ছাপা হত, কিন্তু পাঁচশো কাগজ বাজারে পড়তেই পেল না। সকাল থেকে প্রেস চালিয়ে, সাতগুণ ছেপেও অনেক ‘হকার’কে শেষে ক্ষুণ্ণমনে আর শূন্যহাতে ফিরিয়ে দিতে হল।
সন্ধ্যার পর যখন আপিস থেকে বেরোলাম, দেখলাম একদল লোক আর বালক সামনের রাস্তায় জড়ো হয়েছে; আমাকে দেখেই তারা তৎক্ষণাৎ ফাঁকা হয়ে আমার পথ করে দিল। দু-এক জনকে যেন বলতেও শুনলাম—‘ইনি, ইনিই!’ স্বভাবতই খুব খুশি হয়ে গেলাম। না-হব কেন?
পরদিনও আপিসের সামনে সেইরকম লোকের ভিড়; দল পাকিয়ে দু-চার জন করে এখানে ওখানে ছড়িয়ে, রাস্তার এধারে ওধারে, দূরে সুদূরে (কিন্তু অনতিনিকটে), প্রায় সমস্ত জায়গাটা জুড়েই ব্যক্তিবর্গ। সবাই বেশ আগ্রহের সঙ্গে আমাকে লক্ষ করছে। তাদের কৌতূহলের পাত্র আমি বুঝতে পারলাম বেশ; এবং পেরে আত্মপ্রসাদ হতে লাগল।
আমি কাছাকাছি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জনতা বিচলিত হয়ে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছিল, আমি দ্বিধাবোধ করার আগেই মন্ডলীরা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে আমার পথ পরিষ্কার করে দিচ্ছিল। একজন বলে উঠল—‘ওর চোখের দিকে তাকাও, কীরকম চোখ দেখেছ!’ আমিই যে ওদের লক্ষ এটা যেন লক্ষ করছি না এইরকম ভাব দেখাচ্ছিলাম, কিন্তু সত্যি কথা বলতে কী, মনে মনে বেশ পুলকসঞ্চার হচ্ছিল আমার। ভাবলাম, এ সম্বন্ধে লম্বাচওড়া বর্ণনা দিয়ে আজই বড়দাকে একখানা চিঠি ছেড়ে দেব।
দরজা ঠেলে আপিসঘরে ঢুকতেই দেখলাম দুজন গ্রাম্যগোছের লোক আমার চেয়ার এবং টেবিল ভাগাভাগি করে বসে আছে—বসার কায়দা দেখলে মনে হয় লাঙল ঠেলাই ওদের পেশা। আমাকে দেখেই তারা তটস্থ হয়ে উঠল। মুহূর্তের জন্য যেন তাদের লজ্জায় ম্রিয়মাণ বলে আমার বোধ হল কিন্তু পরমুহূর্তেই তাদের আর দেখতে পেলাম না—ওধারের জানলা টপকে ততক্ষণে তারা সটকেছে। আপিসঘরে যাতায়াতের অমন দরজা থাকতেও তা না ব্যবহার করে অপ্রশস্ত জানলাই-বা তারা কেন পছন্দ করল, এই অদ্ভুত কান্ডের মাথামুন্ড নির্ণয়ে মাথা ঘামাচ্ছি, এমন সময়ে একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক সযত্নলালিত ছড়ি হস্তে আমার সম্মুখে আবির্ভূত হলেন। তাঁর দাড়ির চাকচিক্য দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো। চেয়ারে ছড়ির ঠেসান দিয়ে দাড়িকে হস্তগত করে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—‘আপনি কি নতুন সম্পাদক?’
আমি জানালাম, তাঁর অনুমান যথার্থ।
‘আপনি কি এর আগে কোনো কৃষি-কাগজের সম্পাদনা করেছেন?’
‘আজ্ঞে না’, আমি বললাম, ‘এই আমার প্রথম চেষ্টা।’
‘তাই সম্ভব।’ তিনি পুনরায় প্রশ্ন করলেন, ‘হাতেকলমে কৃষিকাজের কোনো অভিজ্ঞতা আছে আপনার?’
‘একদম না।’ স্বীকার করলাম আমি।
‘আমারও তাই মনে হয়েছে।’ ভদ্রলোক পকেট থেকে ভাঁজ করা এই সপ্তাহের একখানা কৃষি-তত্ত্ব বার করলেন—‘এই সম্পাদকীয় আপনার লেখা নয় কি?’
আমি ঘাড় নাড়লাম—‘এটাও আপনি ঠিক ধরেছেন।’
‘আবার আন্দাজ ঠিক।’ বলে তিনি পড়তে শুরু করলেন—
মুলো জিনিসটা পাড়বার সময় সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক। কখনোই টেনে ছেঁড়া উচিত নয়, ওতে মুলোর ক্ষতি হয়। তার চেয়ে বরং একটা ছেলেকে গাছের ওপরে পাঠিয়ে দিয়ে ডালপালা নাড়তে দিলে ভালো হয়। খুব কষে নাড়া দরকার। ঝাঁকি পেলেই টপাটপ মুলোবৃষ্টি হবে, তখন কুড়িয়ে নিয়ে ঝাঁকা ভরো।…
‘এর মানে কী আমি জানতে চাই।’ ভদ্রলোকের কন্ঠস্বরে যেন উষ্মার আভাস ছিল।
‘কেন? এর মানে তো স্পষ্ট।’ বৃদ্ধ ব্যক্তির বোধশক্তি-হীনতা দেখে আমি হতবাক হলাম, ‘আপনি কি জানেন, কত হাজার হাজার, কত লাখ লাখ মুলো অর্ধপক্ক অবস্থায় টেনে ছিঁড়ে নষ্ট করা হয় আমাদের দেশে? মুলো নষ্ট হলে কার যায় আসে? কেবল যে মুলোরই তাতে অপকার করা হয় তা নয়, আমাদের—আমাদেরও ক্ষতি তাতে। দেশেরই তাতে সর্বনাশ, তার হিসেব রাখেন? তার চেয়ে যদি মুলোকে গাছেই পাকতে দেওয়া হত এবং তারপরে একটা ছেলেকে গাছের ওপরে—’
‘নিকুচি করেছে গাছের! মুলো গাছেই জন্মায় না।’
‘কি! গাছে জন্মায় না! অসম্ভব—এ কখনো হতে পারে? মানুষ ছাড়া সব কিছুই গাছে জন্মায়, এমনকী বঁাদর পর্যন্ত।’
ভদ্রলোকের মুখবিকৃতি দেখে বুঝলাম বিরক্তির তিনি চরম সীমায়। রেগে কৃষি-তত্ত্ব-খানা ছিঁড়ে কুচিকুচি করে ফুঁ দিয়ে, ঘরময় উড়িয়ে দিলেন—তারপরে নিজের ছড়িতে হস্তক্ষেপ করলেন। আমি শঙ্কিত হলাম—লোকটা মারবে নাকি? কিন্তু না, আমাকে ছাড়া টেবিল, চেয়ার, দেরাজ, আলমারি, ঘরের সব কিছু ছড়িপেটা করে, অনেক কিছু ভেঙেচুরে, অনেকটা শান্ত হয়ে, অবশেষে সশব্দে দরজায় ধাক্কা মেরে তিনি সবেগে বেরিয়ে গেলেন। লোকটা কোনো ইশকুলের মাস্টার নয় তো?
আমি অবাক হলাম, ভদ্রলোক ভারি চটে চলে গেলেন তা তো স্পষ্টই, কিন্তু কেন যে কী সম্বন্ধে তাঁর এত অসন্তোষ তা কিছু বুঝতে পারলাম না।
এই দুর্ঘটনার একটু পরেই আগামী সপ্তাহের সম্পাদকীয় লেখবার জন্য সুবিধেমতো জাঁকিয়ে বসছি এমন সময়ে দরজা ফাঁক করে কে যেন উঁকি মারল। যারা জানলা-পথে পালিয়েছিল সেই ‘চষ্য’-রাজাদের একজন নাকি? কিন্তু না, নিরীক্ষণ করে দেখলাম বিশ্রী চেহারার জনৈক বদখত লোক। লোকটা ঘরে ঢুকেই যেন কাঠের পুতুল হয়ে গেল, ঠোঁটে আঙুল চেপে, ঘাড় বেঁকিয়ে, কুঁজো হয়ে কী যেন শোনবার চেষ্টা করল। কোথাও শব্দমাত্র ছিল না। তথাপি সেশুনতে লাগল। তবু কোনো শব্দ নেই। তারপরে অতি সন্তর্পণে দরজা ভেজিয়ে পা টিপে টিপে আমার কাছাকাছি এগিয়ে এসে সুতীব্র ঔৎসুক্যে আমাকে দেখতে লাগল। কিছুক্ষণ একেবারে নিষ্পলক, তারপরেই কোটের বোতাম খুলে হৃদয়ের অভ্যন্তর থেকে একখন্ড কৃষি-তত্ত্ব বার করল।
‘এই যে, তুমি! তুমিই লিখেছ তো? পড়ো—পড়ো এইখানটা, তাড়াতাড়ি। ভারি কষ্ট হচ্ছে আমার।’
আমি পড়তে শুরু করলাম—
মুলোর বেলা যেরকম আলুর বেলা সেরকম করা চলবে না। গাছ ঝাঁকি দিয়ে পাড়লে আলুরা চোট খায়, এই কারণেই আলু পচে আর তাতে পোকা ধরে। আলুকে গাছে বাড়তে দিতে হবে—যতদূর খুশি সেবাড়ুক। এরকম সুযোগ দিলে এক-একটা আলুকে তরমুজের মতো বড়ো হতে দেখা গেছে। অবশ্য বিলাতেই; এদেশে আমরা আলু খেতেই শিখেছি, আলুর যত্ন নিতে শিখিনি। আলু যথেষ্ট বেড়ে উঠলে এক-একটা করে আলাদা আলাদা ফজলি আমের মতন তাকে ঠুসি-পাড়া করতে হবে।
তবে পেঁয়াজ আমরা আঁকশি দিয়ে পাড়তে পারি, তাতে বিশেষ কোনো ক্ষতি হবে না। অনেকের ধারণা পেঁয়াজ গাছের ফল, বাস্তবিক কিন্তু তা নয়। বরং ওকে ফুল বলা যেতে পারে—ওর কোনো গন্ধ নেই, যা আছে কেবল দুর্গন্ধ। ওর খোসা ছাড়ানো মানেই ওর কোরক ছাড়ানো। এনতার কোরক ওর। পেঁয়াজেরই অপর নাম শতদল।
অতি প্রাচীনকালেও এদেশে ফুলকপি ছিল তার পরিচয় পাওয়া যায়, তবে তাকে আহার্যের মধ্যে তখন গণ্য করা হত না। শাস্ত্রে বলেছে অলাবুভক্ষণ নিষেধ, সেটা ফুলকপি সম্বন্ধেই। আর্যেরা কপি খেতেন না, ওটা অনার্য হাতিদের খাদ্য ছিল। ‘গজভুক্ত কপিত্থ’ এই প্রবাদে তার প্রমাণ রয়েছে।
বাতাবিলেবুর গাছে কমলালেবু ফলানোর সহজ উপায় হচ্ছে এই—
‘ব্যাস, ব্যাস—এতেই হবে।’ আমার উৎসাহী পাঠক উত্তেজিত হয়ে আমার পিঠ চাপড়াবার জন্য হাত বাড়াল। ‘আমি জানি আমার মাথা ঠিকই আছে, কেননা তুমি যা পড়লে আমিও ঠিক তাই পড়েছি, ওই কথাগুলোই। অন্তত আজ সকালে, তোমার কাগজ পড়ার আগে পর্যন্ত ওই ধারণাই আমার ছিল। যদিও আমার আত্মীয়স্বজন আমাকে সবসময়ে নজরে নজরে রাখে তবু এই ধারণা আমার প্রবল ছিল যে মাথা আমার ঠিকই আছে—’
তার সংশয় দূর করার জন্য আমি সায় দিলাম—‘নিশ্চয়! নিশ্চয়!! বরং অনেকের চেয়ে বেশি ঠিক একথাই আমি বলব। এইমাত্র একজন বুড়ো লোক—কিন্তু যাক সেকথা।’
লোকটাও সায় দিল—‘হ্যাঁ, যাক। তবে আজ সকালে তোমার কাগজ পড়ে সে-ধারণা আমার টলেছে। এখন আমি বিশ্বাস করি যে সত্যি সত্যিই আমার মাথাখারাপ। এই বিশ্বাস হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি এক দারুণ চিৎকার ছেড়েছি—নিশ্চয়ই তুমি এখানে বসে তা শুনতে পেয়েছ?’
আমি ঘাড় নাড়লাম, কিন্তু আমার অস্বীকারোক্তিতে সেআমল দিল না—‘নিশ্চয় পেয়েছ। দু-মাইল দূর থেকে তা শোনা যাবে। সেই চিৎকার ছেড়েই এই লাঠি নিয়ে আমি বেরিয়েছি, কাউকে খুন না করা পর্যন্ত স্বস্তি হচ্ছে না। তুমি বুঝতেই পারছ আমার মাথার যা অবস্থা তাতে একদিন না একদিন কাউকে না কাউকে খুন আমায় করতেই হবে—তবে আজই তা শুরু করা যাক-না কেন?’
কী জবাব দেব ভেবে পেলাম না, একটা অজানা আশঙ্কায় বুক দুরদুর করতে লাগল।
‘বেরোবার আগে আর একবার তোমার প্যারাগুলো পড়লাম, সত্যিই আমি পাগল কি না নিশ্চিত হবার জন্যে। তার পরক্ষণেই বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিয়ে আমি বেরিয়ে পড়েছি। রাস্তায় যাকে পেয়েছি তাকেই ধরে ঠেঙিয়েছি। অনেকে খোঁড়া হয়েছে, অনেকের মাথা ভেঙেছে; সবশুদ্ধ কতজন হতাহত বলতে পারব না। তবে একজনকে জানি, সেগাছের উপর উঠে বসে আছে। গোলদিঘির ধারে। আমি ইচ্ছা করলেই তাকে পেড়ে আনতে পারব। এই পথ দিয়ে যেতে যেতে মনে হল তোমার সঙ্গে একবার মোলাকাত করে যাই—’
হৃৎকম্পের কারণ এতক্ষণে আমি বুঝতে পারলাম—কিন্তু বোঝার সঙ্গে সঙ্গে হৃৎকম্প একেবারেই বন্ধ হবার জোগাড় হল যেন!
‘কিন্তু তোমায় আমি সত্যি বলছি, যে লোকটা গাছে চেপে আছে তার কপাল ভালো। এতক্ষণ তবু বেঁচে রয়েছে বেচারা। ওকে খুন করে আসাই উচিত ছিল আমার। যাক, ফেরার পথে ওর সঙ্গে আমার বোঝাপড়া হবে। এখন আসি তাহলে—নমস্কার!’
লোকটা চলে গেলে ঘাম দিয়ে আমার জ্বর ছাড়ল। কিন্তু এতগুলো লোক যে আমার লেখার জন্যই খুন-জখম হয়েছে হাত-পা হারিয়েছে এবং একজন গোলদিঘির ধারে এখনও গাছে চেপে বসে আছে—এইসব ভেবে মন ভারি খারাপ হয়ে গেল। কিন্তু অচিরেই এইসব দুশ্চিন্তা দূরীভূত হল, কেননা কৃষি-তত্ত্ব-এর আটপৌরে সম্পাদক অপ্রত্যাশিতরূপে প্রবেশ করলেন।
সম্পাদকের মুখ গম্ভীর, বিষণ্ণ, বিলম্বিত। চেঞ্জে গিয়েই অবিলম্বে ফিরে আসার জন্যই বোধ হয়। আমরা দুজনেই চুপচাপ। অনেকক্ষণ পরে একটিমাত্র কথা তিনি বললেন—‘তুমি আমার কাগজের সর্বনাশ করেছ।’
আমি বললাম, ‘কেন, কাটতি তো অনেক বেড়েছে।’
‘হ্যাঁ, কাগজ বহুত কেটেছে, আমি জানি। কিন্তু আমার মাথাও কাটা গেছে সেইসঙ্গে।’ তারপরে দাড়িওয়ালা ভদ্রলোকের কীর্তিকলাপ তাঁর দৃষ্টিগোচর হল, চারিদিকে ভাঙাচোরা দেখে তিনি নিজেও যেন ভেঙে পড়লেন—‘সত্যি বড়ো দুঃখের বিষয়, বড়োই দুঃখের বিষয়।’ কৃষি-তত্ত্ব-এর সুনামের যে হানি হল, যে বদনাম হল তা বোধ হয় আর ঘুচবে না। অবিশ্যি কাগজের এত বেশি বিক্রি এর আগে কোনোদিন হয়নি বা এমন নামডাকও চারধারে ছড়িয়ে পড়েনি—কিন্তু পাগলামির জন্য বিখ্যাত হয়ে কী লাভ? একবার জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দ্যাখো দেখি চারধারে কীরকম ভিড়—কী শোরগোল। তারা সব দাঁড়িয়ে আছে তোমাকে দেখবার জন্যে। তাদের ধারণা তুমি বদ্ধপাগল। তাদের দোষ কী? যে তোমার সম্পাদকীয় পড়বে তারই ওই ধারণা বদ্ধমূল হবে। তুমি যে চাষবাসের বিন্দুবিসর্গও জান তা তো মনে হয় না। কপি আর কপিত্থ যে এক জিনিস একথা কে তোমাকে বলল? গোল আলুর সম্বন্ধে তুমি যে গবেষণা করেছ, মুলো চাষের যে আমূল পরিবর্তন আনতে চেয়েছ সে-সম্বন্ধে তোমার কোনোই অভিজ্ঞতা নেই। তুমি লিখেছ শামুক অতি উৎকৃষ্ট সার, কিন্তু তাদের ধরা অতি শক্ত। মোটেই তা নয়, শামুক মোটেই সারবান নয়, এবং তাদের দ্রুতগতির কথা এই প্রথম জানা গেল। কচ্ছপেরা সংগীতপ্রিয়, রাগরাগিণীর সম্মুখে তারা মৌনী হয়ে থাকে, সেটা তাদের মৌনসম্মতির লক্ষণ, তোমার এ মন্তব্য—একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক। কচ্ছপদের সুরবোধের কোনোই পরিচয় এ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। এমনিই ওরা চুপচাপ থাকে, মৌনী হয়ে থাকাই ওদের স্বভাব—সংগীতের কোনো ধারই ধারে না তারা। কচ্ছপদের দ্বারা জমি চষানো অসম্ভব—একেবারেই অসম্ভব। আপত্তি না করলেও জমি তারা চষবে না—তারা তো বলদ নয়। তুমি যে লিখেছ, ঘোড়ামুগ ঘোড়ার খাদ্য আর কলার বিচি থেকে কলাই হয়, তার ধাক্কা সামলাতে আমার কাগজ উঠে না গেলে বঁাচি। গাছের ডাল আর ছোলার ডালের মধ্যে যে প্রভেদ আছে দেড় পাতা খরচ করে তা বোঝাবার তোমার কোনোই দরকার ছিল না। কেবল তুমি ছাড়া আর সবাই জানে। যাক, যা হবার হয়েছে, এখন তুমি বিদায় নাও। তোমাকে আর সম্পাদকতা করতে হবে না। আমার আর বায়ুপরিবর্তনের কাজ নেই—ঘাটশিলায় গিয়েই আমাকে দৌড়ে আসতে হয়েছে—তোমার পাঠানো কাগজের কপি পেয়ে অবধি আমার দুশ্চিন্তার শেষ ছিল না। পরের সপ্তাহে আবার তুমি কী গবেষণা করে বসবে সেই ভয়েই আমার বুক কেঁপেছে। বিড়ম্বনা আর কাকে বলে! যখনই তোমার ঘোষণার কথা ভেবেছি—জাম, জামরুল আর গোলাপজাম কী করে একই গাছে ফলানো যায়, পরের সংখ্যাতেই তুমি তার উপায় বলে দেবে, তখন থেকেই নাওয়া-খাওয়া আমার মাথায় উঠেছে—বেরিবেরিতে প্রাণ যায় সেও ভালো—তখনই আমি কলকাতার টিকেট কিনে গাড়িতে চেপেছি।’
এতখানি বক্তৃতার পর ভদ্রলোক এক দারুণ দীর্ঘশ্বাস মোচন করলেন। ওরই কাগজের কাটতি আর খ্যাতি বাড়িয়ে দিলাম, আয়ও বেড়ে গেল কত অথচ উনিই আমাকে গালমন্দ করছেন! ভদ্রলোকের নেমকহারামি দেখে আমার মেজাজ বিগড়ে গেল। অতএব, শেষবিদায় নেওয়ার আগে আমিই-বা ক্ষান্ত হই কেন? আমার বক্তব্য আমিও বলে যাব। এত খাতির কীসের?
‘বেশ, আমার কথাটাও শুনুন তবে। আপনার কোনো কান্ডজ্ঞানই নেই, আপনি একটি আস্ত বঁাধাকপি। এরকম অনুদার মন্তব্য এতক্ষণ আমাকে শুনতে হবে বলে কোনোদিন আমি কল্পনাও করিনি। কাগজের সম্পাদক হতে হলে কোনো কিছু জানতে হয় তাও আমি এই প্রথম জানলাম। এতদিন তো দেখে আসছি যারা বই লিখতে জানে না তারাই বইয়ের সমালোচনা করে, আর যারা ফুটবল খেলতে পারে না তারাই ফুটবল খেলা দেখতে যায়। আপনি নিতান্তই শালগম, তাই একথা বুঝতে আপনার বেগ পেতে হচ্ছে। যদি নেহাত ভূমিকুষ্মান্ড না হতেন তাহলে অবশ্য বুঝতেন যে কৃষি-তত্ত্ব-এর কী উন্নতি আর আপনার কতখানি উপকার আমি করেছি! আমার গায়ে জোর থাকলে আপনার মতো গাজরকে ভালো করে বুঝিয়ে দিয়ে যেতাম! কী আর বলব আপনাকে, পালং শাক, পানফল, তালশাঁস, যা খুশি বলা যায়। আপনাকে পাতি লেবু বললে পাতি লেবুর অপমান করা হয়—’
দম নেবার জন্য আমাকে থামতে হল। গায়ের ঝাল মিটিয়ে গালাগালের শোধ তুললাম, কিন্তু ভদ্রলোক একেবারে নির্বাক। আবার আরম্ভ করলাম আমি—
‘হ্যাঁ, একথা সত্যি, সম্পাদক হবার জন্য জন্মাইনি! যারা সৃষ্টি করে আমি তাদেরই একজন, আমি হচ্ছি লেখক। ভুঁইফোড় কাগজের সম্পাদক হয় কারা? আপনার মতো লোক—নিতান্তই যারা টম্যাটো। সাধারণত যারা কবিতা লিখতে পারে না, আট আনা সংস্করণের নভেলও যাদের আসে না, পিলে-চমকানো থিয়েটারি নাটক লিখতেও অক্ষম, প্রথম শ্রেণির মাসিক পত্রেও অপারগ তারাই অবশেষে হাত-চুলকানো থেকে আত্মরক্ষার জন্য আপনার মতো কাগজ বের করে বসে। আপনি আমার সঙ্গে যেরকম ব্যবহার করেছেন তাতে আর মুহূর্তও এখানে থাকতে আমার রুচি নেই! এই দন্ডেই সম্পাদকগিরিতে আমি ইস্তফা দিচ্ছি। ‘চাষাড়ে’ কাগজের সম্পাদকের কাছে ভদ্রতা আশা করাই বাতুলতা! ঘড়ির দুর্দশা দেখেই আমার শিক্ষা হওয়া উচিত ছিল। যাব তো আমি নিশ্চয়, কিন্তু জানবেন, আমার কর্তব্য আমি করে গেছি, যা চুক্তি ছিল তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি আমি। বলেছিলাম আপনার কাগজ সর্বশ্রেণির পাঠ্য করে তুলব—তা আমি করেছিও। বলেছিলাম আপনার কাগজের কুড়ি হাজার গ্রাহক করে দেব—যদি আর দু-সপ্তাহ সময় পেতাম তাও আমি করতে পারতাম। এখন—এখনই আপনার পাঠক কারা? কোনো চাষের কাগজের বরাতে যা কোনোদিন জোটেনি সেইসব লোক আপনার কাগজের পাঠক—যত উকিল, ব্যারিস্টার, ডাক্তার, মোক্তার, হাইকোর্টের জজ, কলেজের প্রফেসার, যত সব সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। একজনও চাষা নেই ওর ভেতর—যত চাষা গ্রাহক ছিল তারা সব চিঠি লিখে কাগজ ছেড়ে দিয়েছে—ওই দেখুন টেবিলের ওপর চিঠির গাদা! কিন্তু আপনি এমনই চালকুমড়ো যে পাঁচশো মুখ্যু চাষার জন্যে বিশ হাজার উচ্চশিক্ষিত গ্রাহক হারালেন! এতে আপনারই ক্ষতি হল, আমার কী আর! আমি চললাম।’